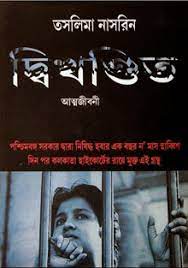- বইয়ের নামঃ দ্বিখণ্ডিত
- লেখকের নামঃ তসলিমা নাসরিন
- বিভাগসমূহঃ আত্মজীবনী
০১. ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে
গ্রাম ছেড়ে শহরে ঢুকেছে কলেরা রোগ। পানি ফুটিয়ে খাচ্ছে মানুষ। পানি শোধনের বড়ি মাগনা বিলোনো হচ্ছে হাসপাতাল থেকে, এমনকী পৌরসভা থেকেও। বড়ি গুলে পানি খাওয়ার উপদেশ বিতরণ করে মাইক মারা হচ্ছে, পৌরসভার কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বড়ি বিলোচ্ছে, তারপরও মহামারি লেগে গেল। ঘরে ঘরে কলেরা রোগী। রাস্তাঘাটে রোগী মরছে। হাসপাতালগুলো উপচে পড়েছে রোগীতে। পর্যাপ্ত বিছানা নেই, মেঝেয় শুইয়ে দেওয়া হচ্ছে রোগীদের, প্রত্যেকের হাতে সুঁই ফুটিয়ে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে কলেরা স্যালাইন। ডাক্তার নার্স সকলে ব্যস্ত। সূর্যকান্ত হাসপাতালে আমিও ব্যস্ত। দৌড়োচ্ছি রোগীদের কাছে স্যালাইন হাতে। বানের জলের মত রোগী আসছে, ওয়ার্ডে জায়গা হচ্ছে না, বারান্দায় শোয়ানো হচ্ছে। রাত দিন স্যালাইন চলছে তারপরও খুব কম রোগী সুস্থ হয়ে উঠছে। হাসপাতালের সামনে মড়া বহন করার খাটিযার স্তূপ। কবরখানায় ভিড়। গুদারাঘাটে ভিড়। আকাশে শকুনের ওড়াওড়ি।
হাসপাতালে কলেরার চিকিৎসা করতে করতে আমার সকাল কখন বিকেল হচ্ছে, বিকেল কখন সন্ধ্যে বুঝে উঠতে পারি না। সন্ধের পর বাড়ি ফিরি, কখনও খুব ক্লান্ত হয়ে গেলে বিকেলেই ফিরি। অবকাশের সামনের নর্দমায় বাবা ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছেন। পানি শোধনের বড়ি শুধু খাবার পানিতে নয়, বাসন ধোয়ার, গোসল করার, কাপড় ধোয়ার সব পানিতেই গুলে দেওয়া হয়েছে। আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেই মা আমার গা থেকে অ্যাপ্রোন খুলে ধুতে নিয়ে যান। সেই বিকেলে আর অ্যাপ্রোন খোলা হয় না, কারণ বাড়ি ফিরতেই বাবা বললেন আমাকে কলে যেতে হবে। তাঁর যাবার কথা ছিল কিন্তু খুব মুমুর্ষু এক রোগীকে তিনি দেখতে যাচ্ছেন। কলে আমি আগে কখনও যাইনি, কলটি কোত্থেকে এসেছে জানতে চাইলে বাবা ঠিকানা বলেন। নওমহল যেতে গিয়ে মেথরপট্টির রেললাইন পার হয়ে তিনটে বাড়ি পরে হাতের বাঁদিকে একটি সাদা বাড়ি। রেহানাদের বাড়ি। রেহানা ইয়াসমিনের বান্ধবী। ইয়াসমিনকে নিয়েই রওনা হই কলে। ডাক্তারি জীবনের প্রথম কলে। অ্যাপ্রোনের পকেটে স্টেথোসকোপ, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র আর কিছু জীবন রক্ষাকারী ইনজেকশন নিয়েছি। রেহানাদের বাড়ির সবাই বাবার জন্য অপেক্ষা করছিল, বাবার বদলে আমি এসেছি, যেহেতু আমিও ডাক্তার, আমাকে দেখানো হল রোগী। রোগিটি রেহানার ছোট ভাই। চোখ গর্তে চলে গেছে, ঠোঁট জিভ শুকিয়ে চচ্চড় করছে। ডিহাইড্রেশন পরীক্ষা করে কোনওরকম দেরি না করে রোগীকে হাসপাতালে নিতে বলি। হাসপাতাল থেকে জায়গার অভাবে রোগী ফেরত দেওয়া হচ্ছে, এ কথাটি রেহানার একটি সুস্থ ভাই বলল পাশ থেকে। ছেলেটিকে হাসপাতালে নিতে বাড়ির কেউই রাজি নয়। অগত্যা পাঁচ ব্যাগ কলেরা স্যালাইন, স্যালইন সেট, বাটারফ্লাই নিডল আর কিছু ওষুধপত্রের নাম লিখে দিই কাগজে, রেহানা সুস্থ ভাইটিকে টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় জলদি জলদি সব কিনে নিয়ে আসতে। বাড়িটির দোতলায় ছোট্ট দুটো ঘর, ঘরের জিনিসপত্র সব এলো মেলো, রেহানার বাবা পা গুটিয়ে উদভ্রান্ত বসে আছেন একটি চেয়ারে। রেহানার মা মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়, কোলে ব্যারিস্টার, ব্যারিস্টার রেহানার তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ভাই। ব্যারিস্টারের এর মধ্যে দুবার বাস্তু গেছে। রেহানা ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যারিস্টারকেও ধরেছে কি না রোগে। সুস্থ ভাইটি স্যালাইন নিয়ে এলে আমি স্যালাইন রানিং চালিয়ে দিয়ে রেহানাকে বুঝিয়ে দিই কি করে স্যালাইনের এক ব্যাগ শেষ হয়ে গেলে আরেক ব্যাগ লাগিয়ে দিতে হবে। সোফার ভাই এবং ব্যারিস্টার দুজনকেই কোনও দ্বিধা না করে হাসপাতালে নিয়ে যাবার উপদেশ আবারও বর্ষণ করে যখন দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি, রেহানা আসে আমার পেছন পেছন। ইয়াসমিন আমার আগে বেরিয়ে একটি রিক্সা ডেকে উঠে বসেছে। রেহানার সঙ্গে ইয়াসমিনের তুই তোকারি সম্পর্ক। ইশকুলে এক সঙ্গে পড়েছে ওরা। কিছু মেয়ের ইশকুলে পড়াকালীনই বিয়ে হয়ে যায়, রেহানা সেরকম। দেড়বছরের একটি মেয়ে আছে রেহানার। নিজের সংসার ফেলে বাপের বাড়ি চলে এসেছে ভাইদের সেবা করতে। রেহানা নিজের মেয়েটিকে দেখতে যেতে পারছে না দুদিন, মেয়েটিকে এ বাড়িতে নিয়ে আসাও নিরাপদ নয়। সিঁড়ির শেষ মাথায় নেমে রেহানা আমাকে টাকা দিল। ষাট টাকা। ডাক্তারের ফি। কলে গিয়ে আমার প্রথম উপার্জন। উপার্জনটি করে রিক্সায় উঠে ইয়াসমিনকে সোল্লাসে বলি। ইয়াসমিন হাঁ হয়ে, ভুরু কুঞ্চিত, আমার হাসি-মুখের দিকে কিছুক্ষণ হতভম্ব তাকিয়ে থেকে বলল, ‘তুমি রেহানার কাছ থেইকা টাকা নিছ?’ আমি হাসি-মুখেই বলি, ‘হ। নিছি। নিব না কেন? দিল তো! রোগী দেইখা দিছি। টাকা নিব না কেন?’
‘রেহানা তো আমার বান্ধবী। বাড়িতে দুই ভাই কলেরায় ভুগতাছে। এইসময় তুমি পারলা কি ভাবে টাকা নিতে?’
টাকাটা যখন বাড়িয়েছিল রেহানা, টাকা নেবার অভ্যেস নেই বলে আমার আড়ষ্টতা ছিল। রেহানা ইয়াসমিনের বান্ধবী হলেও আমার তো কেউ নয়! শহর খুঁজলে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ওরকম আমার বা ইয়াসমিনের বান্ধবী, দাদার বা ছোটদার বন্ধু, বাবা আর মার চেনা বা লতায় পাতায় আত্মীয় পাওয়া যাবে তাহলে তো ডাক্তরি করে টাকা পয়সা উপার্জন সম্ভব হবে না! কলে এসেছি, রিক্সাভাড়া খরচা হয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছি, শ্রম ঢেলেছি, ফি নেবারই তো কথা। সব ডাক্তারই নেয়। এসব ভেবে মন শক্ত করে রেহানার বাড়িয়ে দেওয়া টাকাটি শেষ পর্যন্ত নিয়েছি আমি। নিতে তারপরও সংকোচ হয়েছে, চোখ মুখ মাথা সবই নত হয়েছে আপনাতেই। বুকের ভেতরটা ঠান্ডা হয়ে এসেছে, কিন্তু নিয়েছি। সারা পথ ইয়াসমিন ভুরু কুঞ্চিত করেই রেখেছে, কথা বলেনি আমার সঙ্গে। বলেছি, চল, শ্রীকৃষ্ণে গিয়া মিষ্টি খাইয়া আসি। বলেছে, না। বলেছি, চল সিনেমা দেখি। বলেছে, না। ভেবেছিলাম বাড়িতে আমার প্রথম কলের উপার্জনের খবরটি জানালে বাড়ির সবাই খুশি হবে। কিন্তু কারও মুখে খুশির চিহ্ন নেই এমনকী বাবার মুখেও নেই। বাবা বললেন, আমি তো টাকা নিই না। ওদের ফ্রি দেখি। বাবা এরকম ফি ছাড়া প্রচুর রোগী দেখেন শহরে। বাবা দেখেন বলে আমার দেখতে হবে তা তো নয়।
পরদিন বাবা খবর দিলেন রেহানার ছোট ভাই ব্যারিস্টারকেও ধরেছে কলেরায়। সুস্থ ভাইটিকেও ধরেছে। তিন ভাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালে। রেহানা আর রেহানার বাবা দৌড়োদৌড়ি করে সব করছে। এর পরদিন বাবা যা বললেন, তা শুনে আমরা বিশ্বাস করিনি যে বাবা আদৌ সত্য কোনও কথা বলছেন। বললেন, রেহানার তিন ভাই হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফেরত এসেছে, কিন্তু রেহানা আর রেহানার বাবা মারা গেছে। দুজনকেই তড়িঘড়ি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল শেষ রাতের দিকে, কিন্তু লাভ হয়নি। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা গেছেন রেহানার বাবা। রেহানা মারা গেছে হাসপাতালে পৌঁছোনোর আধঘণ্টা পর। রেহানা যখন ভাইদের সেবা করছিল, কাউকে বলেনি যে তারও বাস্তু বমি হচ্ছে। সে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে ভাইদের সেবা করবে কে! হাসপাতালে নেবে কে! তাই বলেনি। রেহানা চায়নি তাকে নিয়ে কেউ ব্যস্ত হোক। তার বাবাও গোপন করেছেন নিজের বাস্তু বমির কথা। তিনিও কাউকে বুঝতে দিতে চাননি। ছেলেরা সুস্থ হোক, তারপর তিনি নিজের কথা ভাবতে চেয়েছিলেন।
রেহানার বাবাই ছিলেন সংসারের একমাত্র রোজগেরে লোক। নীতিবান লোক ছিলেন বলে উকিলের চাকরি করেও সংসারের অভাব দূর করতে পারেননি। রেহানা যখনই পেরেছে, স্বামীর উপার্জন থেকে যাই হোক কিছু বাঁচিয়ে বাপের সংসারে দিয়েছে। এখন কী হবে সংসারের মানুষগুলোর! এ নিয়ে অবকাশের আর সবাই আলোচনা করতে বসলেও আমি নিস্পন্দ বসে থাকি, আমার ভাবনায় স্থির হয়ে আছে রেহানার ফর্সা গোল মুখটি, উদ্বিগ্ন কিন্তু উজ্জ্বল সেই মুখটি, মলিন কিন্তু মায়াবী মুখটি। নিজেকে বার বার আমি প্রশ্ন করতে থাকি, রেহানার ওই টাকা আমি কেন নিয়েছিলাম? কী প্রয়োজন ছিল আমার টাকার? অভাবের সংসারে ষাট টাকা অনেক টাকা। রেহানার নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল ওই টাকার। নিশ্চয়ই সে ভেবেছিল, টাকা আমি নেব না, আমি তার বান্ধবীর বোন, আমার বাবা ও বাড়ির সবাইকে বিনে পয়সায় চিকিৎসা করেন। যখন আমি লোভীর মত, অবিবেচকের মত, কলেরা আক্রান্ত একটি বাড়ির চরম দুঃসময়ে, বড় টালমাটাল অস্থির সময়ে টাকাটা নিয়েছি, নিশ্চয়ই রেহানা অবাক হয়েছিল, কষ্ট পেয়েছিল। দুদিন পর মরে যাবে মেয়ে, তাকে কেন আমি কষ্ট দিয়েছি! কি দরকার ছিল কষ্ট দেওয়ার! ওই ষাট টাকা নিশ্চয়ই অনেক কষ্টে তার নিজের জমানো টাকা থেকে দিয়েছিল আমাকে। কত টাকা উল্টোপাল্টা খরচ করি আমি। টাকার হিসেব করি না কোনওদিন। আর ওই অভাবের সংসার থেকে ওই কটা টাকা আমার না নিলে কী এমন হত! আমি কি মরে যেতাম! না খেয়ে থাকতে হত আমাকে! না হত না। আমি মরেও যেতাম না। আমার তো এমন কোনও প্রয়োজন ছিল না টাকার! শখে নিয়েছি, সুখে নিয়েছি। ডাক্তারির গর্বে নিয়েছি। কলে গেছে ডাক্তার, ফি না নিলে তো নিজেকে ডাক্তার ডাক্তার মনে হয় না, তাই নিয়েছি। নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। আয়নায় নিজের চেহারাটি বড় কুৎসিত লাগে, ঘৃণা ছুঁড়ে দিই। নিজের কুৎসিত নিষ্ঠুর হাতটির দিকে ঘৃণা ছুঁড়তে থাকি, যে হাত ওই টাকা স্পর্শ করেছিল। নিজের অপকর্মের জন্য নিজেরই ভুরু কুঞ্চিত হয়, নিজের দিকেই তাকিয়ে বলি, ‘তুই নিতে পারলি টাকা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এত লোভ তোর! ছিঃ!’
মা কোনওদিন রেহানাকে দেখেননি। কিন্তু ইয়াসমিনের সঙ্গে মা গেছেন রেহানাদের বাড়িতে। আমিই যাইনি। যাওয়ার মুখ নেই বলে যাইনি। মা রেহানাদের বাড়ি থেকে কেঁদে কেটে চোখ ফুলিয়ে ফিরে এলেন।
ইয়াসমিন এর পর থেকে পানি দেখলেই ভয়ে দু হাত দূরে ছিটকে সরে যায়। ওকে জলাতংক রোগে ধরে। তেষ্টা পেলেও পানি খায় না, ঘামে গরমে শরীরের বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা হলেও গোসল করতে যায় না। যতই ইচ্ছে করি, জীবনকে অতীতে ফিরিয়ে নিতে পারি না। অপরাধবোধ আমাকে নিবিড় করে আলিঙ্গন করে। আমি যেখানেই যাই, যায়। আমি স্থির হয়ে বসে থাকি, অপরাধবোধটিও থাকে, বসে থাকে। এই বোধটি কখনও আমার জীবন থেকে যাবে না আমি জানি।
একসময় কলেরার প্রকোপ দূর হয় শহর থেকে। কিন্তু বছর কুড়ি বয়সের রেহানা নেই আর এ শহরে। কেউ তাকে কোনওদিন ফিরে পাবে না। আমিও কোনওদিন নিজের ভূল শুধরে নেওয়ার জন্য একটি দিন ফিরে পাবো না। যে দিন যায়, যায়। আমি এক ঘোরের মধ্যে ডুবে থাকি। যদিও মার হাতে দুশ টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম রেহানার মার জন্য, আমার গ্লানিবোধ সামান্যও কমেনি। রেহানা তো জানেনি যে টাকা আমি ফেরত পাঠিয়েছি। কোনওদিনই সে জানবে না। ভাবতে থাকি, রেহানার হাত থেকে ওই টাকা নেওয়াটি ঘটেনি জগতে, ওটি কেবলই আমার দুঃস্বপ্ন। রেহানাদের বাড়ির সিঁড়ির কাছে একটি দৃশ্য আমার ভাবনার মধ্যে দোল খেতে থাকে। রেহানা আমাকে সাধছে টাকা, আমি তার কাঁধে হাত রেখে বলছি, ‘তুমি কি পাগল হইছ? আমি টাকা নিব কেন? টাকা রাইখা দেও,কাজে লাগবে।’ রেহানা হেসে বলছে, ‘অনেক ধন্যবাদ নাসরিন আপা। খুব উপকার করলেন আমাদের। ভাইটার চিকিৎসা করে দিলেন। আপনার এই ঋণ কোনওদিন শোধ করতে পারব না।’ চোখদুটোতে তার কৃতজ্ঞতা ছলছল করছে। দোল খেতে থাকে আরেকটি দৃশ্য। রেহারার ভাইদুটো সুস্থ হয়ে উঠেছে। রেহানা তার ভাইদের নিয়ে লুডু খেলতে বসেছে। রেহানার মেয়েটি পাশে বসে লুডু খেলা দেখছে। রেহানার ফর্সা চঞ্চল মুখটি থেকে বিষণ্নতা কেটে গেছে, মুখটি হাসছে, কাজল কালো চোখদুটো হাসছে।
সূর্যকান্ত হাসপাতালে কলেরা দূর হওয়ার পর কাজ তেমন নেই। ময়মনসিংহ জেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফিরে গিয়ে আমি আবদার করি কোথাও কোনও কাজের জায়গায় আমাকে যেন নিয়োগ করা হয়। কেন্দ্রের পরিচালক নূরুল হক বললেন, ‘পরিবার পরিকল্পনা আপিসে যোগ দাও। ওখানে একটা ডাক্তারের পোস্ট খালি আছে।’ তুমি যোগ দাও পরিবার পরিকল্পনা আপিসে যেন কিছু ব্যস্ততা যোগ হয় তোমার জীবনে। কিন্তু এই আপিসটি তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখে তার নিজস্ব ভূবন থেকে। নিজস্ব ভূবনটির ভেতরে তুমি ঢুকতে চাও, কিন্তু অদৃশ্য এক দোররক্ষী তোমাকে যেতে দেয় না। তুমি পাঁচশ সিরিঞ্জকে পাঁচশ সিরিঞ্জই বোঝো, পাঁচশকে পঁচিশ বোঝো না, পঁচিশ আর পাঁচশর প্যাঁচটি বুঝতে পারো না বলে তোমাকে দলে নেওয়া হয় না। তুমি দলছুট হয়ে একা বসে থাকো। একা একা তুমি কাজ খোঁজো। তোমার কাজের জন্য তুমি দেখ কিছু নেই। তোমার জন্য আলাদা কোনও ঘর নেই, তোমার কোনও আলাদা টেবিল চেয়ার নেই, তোমার কোনও রোগী নেই যে দেখবে। আপিসের কেরানিরা বসে থাকেন সামনে কাগজ, কলম আর নানা রঙের নথিপত্র নিয়ে। কি আছে এসব নথিপত্রে, কী করে এই আপিসটি চলছে, তা বুঝতে চেয়ে তুমি বোকা বনে যাও। বোকা বনে যাও, কারণ এই আপিসের নাড়িনক্ষত্র জানার অধিকার তোমাকে দেওয়া হয় না। তোমাকে শুধু বসে থাকতে বলা হয় এবং খামোকাই বসে থাকতে বলা হয়। তোমার নিজেকে মনে হতে থাকে তুমি একটি বাড়তি মানুষ। আসলেই তুমি বাড়তে মানুষ, আপিসের কর্তা হচ্ছেন ফর্সা লম্বা ধোপ দুরস্ত মুজিবর রহমান, পরিবার পরিকল্পনা অফিসার। তিনি ডাক্তারির ড ও জানেন না, কারণ তিনি ডাক্তার নন। মুজিবর রহমানের পছন্দমত এই আপিস চলবে, তুমি শুধু শোভা বর্ধনের জন্য। তুমি ছাড়াও আরও একজন ডাক্তার আছেন পরিবার পরিকল্পনায়, মোটাসোটা গোলগাল সাইদুল ইসলাম। সাইদুল ইসলামের সঙ্গে মুজিবর রহমানের বেশ ভাব। তাঁদের ফিসফিস খিলখিল তোমার নজরে পড়ে। সাইদুল ইসলাম এই আপিসে ঠিক শোভা বর্ধনের জন্য নন। তিনি পরিবার পরিকল্পনার ডিজি অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেলের আপিসের ডাক্তার, এখানে মাঝে মধ্যে ঢুঁ দেন। মোটর সাইকেলে চড়ে তিনি এদিক ওদিক দৌড়োন, খোঁজ নেন ওষুধপত্রের, সই করেন কাগজে। পরিবার পরিকল্পনার আপিসটি কালিবাড়ি রোডের ওপর। বড় একটি টিনের ঘর, অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে গেছে নিচু উঠোনটিতে, উঠোনের তিন কোণে বড় ঘরটির তুলনায় ছোট তিনটি টিনের ঘর। তিনটি ছোট ঘরের একটি খালি, একটি ওষুধপত্র রাখার ঘর, আরেকটি ঘর আয়েশা খাতুনের বসার জন্য। আয়শা খাতুনের কাজ হল যারাই জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি বা কনডম নিতে আসে, দেওয়া। কয়েল পরতে আসে মেয়েরা, পর্দার আড়ালে নিয়ে পরিয়ে দেন, খুলতে আসে, খুলে দেন। আয়েশা খাতুন তোমার মার সঙ্গে এক ইশকুলে পড়তেন। এটি জেনে তুমি দুজনকে মেলাবে, একজন মাটির চুলোয় খড়ি ঠেলছেন, ফুঁকনি ফুঁকছেন, আরেকজন সেজে গুজে আপিসে আসছেন, এই আরেকজনই হয়ত পেছনের বেঞ্চের মেয়ে, শিক্ষক গোবর ইংরেজি কি জিজ্ঞেস করলে মাথা নিচু করে বসে থেকেছেন, ওদিক থেকে ভাল ছাত্রী ঈদুল ওয়ারা ঝটপট উত্তর দিয়েছেন কাউ ডাং, সেই ঈদুল ওয়ারা এখন কাউ ডাং দিয়ে বড়ি বানিয়ে রাখেন চুলোয় আগুন ধরাতে। চৌচালা টিনের ঘরটিতে শক্ত কাগজের দেয়াল দিয়ে দুটো ঘর তৈরি করা হয়েছে, ছোটটিতে বসেন মুজিবর রহমান, বড়টিতে চারজন, চারজনের একজন আম্বিয়া বেগম। কড়া লিপস্টিক মেখে, গালে গোলাপি পাউডার লাগিয়ে নিপাট নিভাঁজ শাড়ি পরে তিনি আপিসে আসেন। তিনি হিসাব রক্ষক। হিসাব রক্ষককে নিয়ে মুজিবর রহমান প্রতিদিনই দুবার কী তিনবার ওষুধের গুদাম ঘরটিতে ঢোকেন ওষুধের হিসাব নিতে। ঘন্টা কেটে যায়, হিসাব নেওয়া শেষ হয় না। কী, ঘটনা কি? সাইদুল ইসলাম, যেহেতু তিনি ডাক্তার, নিজের প্রজাতি, তাঁকেই জিজ্ঞেস কর। তিনি হো হো করে হেসে উঠে বলেন, ঘটনা কী, তা অনুমান করে নেন যদি ক্ষমতা থাকে। এই তোমার দোষ, কল্পনা শক্তি তোমার নেহাতই কম। তুমি খুব বেশি অনুমান করতে পারো না। মুজিবর রহমান যতক্ষণ থাকেন আপিসে, হিসাব নেওয়ার বাইরে তিনি যা করেন তা হল, সহকারীদের ধমকানো আর আম্বিয়াকে ঘরে ডেকে নরম সূরে কথা বলা। সাইদুল ইসলাম আসছেন, যাচ্ছেন। সাইদুল ইসলাম আর মুজিবর রহমান যখন ইচ্ছে আপিসে আসেন, যখন ইচ্ছে চলে যান। সহকারিরাই কেবল বসে থাকেন সকাল দশটা থেকে পাঁচটা। কাজ থাকুক না থাকুক তাঁদের বসে থাকতেই হবে। আম্বিয়া অবশ্য সহকারিদের মধ্যে সুযোগ বেশি পান। আম্বিয়ার ওপর কর্তার সুনজর আছে বলে। আম্বিয়া ইচ্ছে করলে পাঁচটার বেশ আগেই বাড়ি চলে যেতে পারেন। তোমার কাজটি দীর্ঘদিন পর যা আমি আবিস্কার কর, তা হল আয়শা খাতুনের যদি কখনও কোনও কয়েল পরাতে অসুবিধে হয় বা জন্মনিরোধক বড়ি খেয়ে কোনও রোগীর যদি সমস্যা হয় যার তিনি সমাধান জানেন না, তার সমাধান দেওয়া। আয়শা খাতুন অভিজ্ঞ মানুষ, দীর্ঘদিন পরিবার পরিকল্পনায় চাকরি করে তিনি জানেন কি করে সমস্যা সারাতে হয়। আসলে এ ব্যপারে তুমি যত জানো, তার চেয়ে তিনি বেশিই জানেন। যাই হোক, তুমি হচ্ছ আয়শা খাতুনের বস। বস এ তুমি বিশ্বাসী নও। তোমার সম্পর্ক জমে ওঠে কর্মীদের সঙ্গে। গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে আছে কয়েকশ কর্মী। এরা আপিসে আসে প্রায়ই। সভায় ডাক পড়ে অথবা টাকা পয়সা বড়ি কনডম নেওয়ার থাকে শহরের আপিস থেকে। গ্রামে এদের কাজ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে বলা, বিনে পয়সায় বড়ি কনডম বিলি করা, বন্ধাত্বকরণের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। এই কর্মীদের কেউ কেউ ইশকুল পাশ করেছে, কেউ আবার কলেজও। কর্মীদের মধ্যেও ধাপ আছে। কেউ উঁচু পদে, কেউ নিচু পদে। বেশির ভাগ কর্মীই মহিলা, হাতে গোণা অল্প কজন শুধু পুরুষ। পুরুষ, তুমি লক্ষ করেছো, নিচু পদে চাকরি করলেও দাপট দেখানোয় বেশ পারদর্শি। তুমি দেখেছো মুজিবর রহমানের দাপট। অচিরে তাঁর সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয় তোমার। যখন উঠোনের খালি পড়ে থাকা ঘরটিতে রাস্তার এক উদ্বাস্তু দম্পত্তি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে মাথা গোঁজে। মুজিবর রহমান ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে চান ওদের। তুমি সামনে দাঁড়িয়ে বল, ‘ওরা এখানে থাকলে ক্ষতি তো কিছু নেই! এই ঘর তো ব্যবহার হচ্ছে না, থাকুক ওরা!’ মুজিবর রহমান কঠিন কণ্ঠে বলেন, ‘না ওরা থাকবে না, ওরা যাবে।’
‘ওরা যাবে কোথায়? যাবার তো ওদের কোনও জায়গা নেই। কী ক্ষতি যদি থাকে!’ ‘অনেক ক্ষতি, অনেক ক্ষতি।’
কী ক্ষতি, তা মুজিবর রহমান তোমাকে বুঝিয়ে বলেন না। এই বচসায় তুমি হেরে যাও। তোমার চেয়ে মুজিবর রহমানের দাপট বেশি। তিনি পুরুষ। মুজিবর রহমান আর সাইদুল ইসলাম পুরুষ এবং অফিসার হওয়ার দাপটে যখন সন্ত্রস্ত করে রাখে আপিসের সহকারিদের, কর্মীদের, তুমি অফিসার হয়েও মিশে থাকো কেরানি আর কর্মীদের সঙ্গে। তোমাকে অফিসার বলে মনে হয় না, তোমাকে মনে হয় তুমি ওইসব অল্প বেতন পাওয়া মানুষদের একজন। ওদের পাশের বাড়ির মেয়ে তুমি অথবা ওদের খালাতো বোন নয় মামাতো বোন। কর্মীরা তাদের জীবনের খুঁটিনাটি অকপটে বলতে থাকে তোমার কাছে। তুমি শুনতে থাকো। যেহেতু তুমি আপিসের সকলের চাইতে বয়সে ছোট, তোমাকে দেখলেই তোমার দ্বিগুন ত্রিগুণ বয়সের কর্মীদের চকিতে দাঁড়িয়ে স্লামালেকুম ম্যাডাম বললে তুমি অস্বস্তি বোধ কর। যেন এটি না করে কেউ, তুমি অনুরোধ কর। তোমার মায়ের বয়সী আয়শা খাতুনও তুমি ঘরে ঢুকলে দাঁড়িয়ে তোমাকে স্লামালেকুম ম্যাডাম বলতেন, তিনি সোজাসুজি বলে দিয়েছো এই কাজটি করলে তুমি আর ঘরে ঢুকবেই না। তুমি স্বস্তি বোধ কর সহজ মেলামেশায়, কথায়, কৌতুকে। তুমি যত প্রিয় ওঠো নিচুতলায়, তত তুমি অপ্রিয় হও উঁচুতলায়। দেখা যায়, তুমি অফিসার হয়েও অফিসার নও। তুমি, আপিসের পিয়নটি তার মেয়েকে ইশকুলে ভর্তি করাবে কিন্তু টাকা নেই, টাকা দিচ্ছ। কারও টাকা ধার লাগবে, দিচ্ছ এবং ইচ্ছে করেই ভুলে যাচ্ছে! টাকা ফেরত নেওয়ার কথা। কারও চিকিৎসা হচ্ছে না, চিকিৎসার ব্যবস্থা করছ। আপিসে যেহেতু কোনও কাজ নেই, তুমি কাজ খুঁজতে খুঁজতে একটি কাজ নিজে ইচ্ছে করেই নাও। কাজটি মূলত সাইদুল ইসলামের, তিনি মাঝে মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার কর্মীদের নিয়ে গ্রামে গঞ্জে যান স্টেরিলাইজেশন ক্যাম্প করতে। গ্রামের কোনও ইশকুল ঘরে কর্মীদের মাধ্যমে যোগাড় করা মানুষদের লাইগেশন আর ভ্যাসেকটমি করেন তিনি। তুমিও এখন নৌকোয়, রিক্সায়, গরুর গাড়িতে, হেঁটে যেতে থাকো সেসব ক্যাম্পে। লাইগেশন করতে থাকো, ভ্যাসেকটমিও কদাচিৎ কর। ভ্যাসেকটমি যাদের কর, তারা আশি নব্বই বছরের দরিদ্র বুড়ো, রাস্তায় যায় যায় হৃদপিণ্ড নিয়ে হয়ত চিৎ হয়ে পড়ে ছিল, কর্মীরা কাঁধে করে এনে ক্যাম্পে ফেলেছে। পুরুষ সে যে বয়সেরই হোক না কেন, ধন হারাতে চায় না। ক্যাম্পে বিভিন্ন বয়সের মেয়েদেরই ভিড়। তুমি জানতে পারো, যে, যে মেয়েদের ছটি সাতটি করে সন্তান এবং শরীর কাহিল হচ্ছে ঘন ঘন সন্তানজন্মদানে, তারা সকলে বন্ধ্যাকরণে রাজি হলেও ক্যাম্পে আসার অনুমতি পাচ্ছে না। না পাওয়ার কারণ তাদের স্বামী। স্বামীরা মনে করছে আল্লাহ তায়ালা সন্তান দিতে ইচ্ছে করছেন তাই দিচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করা অন্যায়। তুমি জানতে পারো, যে, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলা তো দূরের কথা, সন্তানের মুখে দুবেলা ভাত দেবার যাদের সামর্থ নেই তারাও বছর বছর সন্তান জন্ম দিচ্ছে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ভয়ে বন্ধ্যাকরণের দিকে পা বাড়াচ্ছে না। কর্মীদের বলে দিচ্ছে, আল্লাহ সন্তান দিতাছে, আল্লাহই খাওয়াবো। এও জানতে পারো তুমি, যে, পাঁচটি বা ছটি বা সাতটি সন্তান জন্ম দেবার পরও মেয়েরা গর্ভবতী হচ্ছে, কারণ সেসব মেয়েদের স্বামীরা পুত্রসন্তানের অপেক্ষা করছেন। আরেকটি জিনিস তুমি লক্ষ্য কর, যে, মেয়েরা যারা য়েচ্ছ!য় লাইগেশন করতে আসে, তারা মূলত আসে একটি শাড়ি আর নগদ একশ কুড়ি টাকা পাওয়ার জন্য। সরকার থেকে লাইগেশনের উপহার এই ই দেওয়া হয় কি না। তুমি আবিস্কার করতে থাকো, যে, যদিও যার অন্তত দুটি সন্তান নেই এবং ছোট সন্তানের বয়স অন্তত পাঁচ বছর নয়, তার লাইগেশন করা নিষেধ কিন্তু চরম দারিদ্র অনেক মেয়েদের মিথ্যে বলিয়ে নিয়ে আসে ক্যাম্পে, সে কেবল ওই সরকারি উপহারের জন্য। তুমি এও আবিস্কার কর যে ওই মাত্র একশ কুড়ি টাকা থেকেও ভাগ বসায় কিছু পরিবার পরিকল্পনার দালাল। তুমি আবিস্কার করতে থাকো যে যারা নিজেদের বয়স তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ বলছে এবং নিজেদের দু সন্তানের মা বলছে, তাদের অনেকের বয়স ষোলো কী সতেরো এবং তারা নিঃসন্তান। একটি সস্তা সুতির শাড়ি আর একশ কুড়ি টাকার জন্য তারা সারাজীবনের জন্য বন্ধ্যা হতে চাইছে। তুমি আবিস্কার কর তোমার দেশের দারিদ্র। তুমি শিহরিত হও। তুমি কাঁদো।
০২. খুঁটিনাটি
যে মেয়েটির সঙ্গে কলেজের শেষ দিকে আমার বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল সে শিপ্রা, শিপ্রা চৌধুরি। শিপ্রার দুটি জিনিস আছে, যে জিনিসটি আমাকে আকর্ষণ করে তা তার রসবোধ আর যে জিনিসটি বিকর্ষণ করে তা হল যে কোনও কিছু নিয়ে তার উদ্বিগ্নতা। দেখছে ক্লাসের একটি মেয়ে লিভারের অসুখগুলো পড়ছে শিপ্রা সঙ্গে সঙ্গেই উদ্বিগ্ন, কেন মেয়েটি লিভারের অসুখ পড়ছে, নিশ্চয়ই এ নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে! তক্ষুনি সে রাত জেগে লিভারের অসুখ পড়া শুরু করে দিল। কেউ একজন বলল, হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া না করলে মেডিকেলের লেখাপড়া ঠিক হয় না। যেই না বলা, যদিও বাড়িতে বসে শিপ্রার লেখাপড়া চমৎকার হচ্ছিল, ব্যাগে কাপড় চোপড় ভরে সে হোস্টেলে রওনা হল। শিপ্রার পড়ার সঙ্গী ছিল একটি ছেলে। ভাল ছাত্র হিসেবে ছেলের নাম ছিল। এরপর আরও ভাল ছাত্র হিসেবে যখন আরও কজনের নাম হল, তখন শিপ্রা সেই আরও ভালর দিকে নজর দিতে শুরু করল, মুখ চোখ ওর বিষাদাচ্ছত। কেন সে সেই আরও ভালদের পাচ্ছে না সঙ্গী হিসেবে! শিপ্রার স্বস্তি নেই সহজে। শিপ্রার বাড়ি শহরে। খাগডহর পার হয়ে জেলখানা, জেলখানার কাছে পুরোনো বোম্বাই কলোনি, সেখানে তার মা আর সে থাকে। বাবা অনেক আগেই শিপ্রার মাকে ছেড়ে চলে গেছে। শিপ্রার মা চাকরি করেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। চাপাই নবাবগঞ্জের মানুষ তিনি, বদলির চাকরিতে ঘুরতে ঘুরতে এই ময়মনসিংহে এসে থিতু হয়েছেন। শিপ্রার মাকে দেখলে অগাধ শ্রদ্ধা জাগে। এমন স্বনির্ভর, এমন আত্মপ্রত্যয়ী মা খুব একটা দেখা হয়নি আমার। শিপ্রা এই শহর থেকেই বিদ্যাময়ী পাশ করে আনন্দমোহন পাশ করে মেডিকেলে ঢোকে। এতবছর এ শহরে থেকেও শিপ্রা কথা বলে রাজশাহীর ভাষায়। ময়মনসিংহের ভাষার তুলনায় পরিচ্ছত, সুন্দর। আইবাম, খাইবাম, যাইবাম চন্দনার মত রপ্ত করা শিপ্রার পক্ষে সম্ভব হয় না, এখনও সে আসব খাব যাবতে রয়ে গেছে। তা থাক, শিপ্রা যেমন আছে, তেমন থাকলেই দেখতে ভাল লাগে। শিপ্রা লম্বায় আমার চেয়ে দুইঞ্চি বেশি, মেদ মাংসে আমার চেয়ে কেবল দুইঞ্চি নয়, অনেক ইঞ্চিই বেশি। ক্লাসের সবচেয়ে লম্বা মেয়ে বলে আমার পরিচয়খানি শিপ্রার সামনে এসে খুব ম্লান না হলেও খানিকটা তো হয়ই। এই ম্লানতা আমাকে, আমি লক্ষ্য করেছি, ছুঁতে পারে না।
মাঝে মধ্যে ক্যাম্পে যাওয়া ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা আপিসের চাকরিটি যেহেতু আমার বসে থাকার, তাই শিপ্রার সঙ্গে আমার দেখা হতে থাকে ঘন ঘন, আড্ডা হতে থাকে দীর্ঘ দীর্ঘ। আমি আর শিপ্রা ছাড়া আমাদের ক্লাসের আর কোনও ছেলে বা মেয়ে এই শহরে চাকরি করছে না, শিপ্রা বাউন্ডারি রোডে পঙ্গু সেবালয়ে বসে। তারও কাজ নেই। শহরে বড় একটি হাসপাতাল থাকলে এসব ছোট খাটো জায়গায় বেশি কেউ আসে না। মেডিকেল কলেজের আমরাই শেষ ডাক্তার যারা পাশ করার পরই সরকারি চাকরি পেয়েছি। আমাদের পরের বছর থেকে যারা ডাক্তার হয়ে বেরোচ্ছে, তাদের জন্য আপনাতেই কোনও চাকরি হয়নি। তারা প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোয় ঘুরছে চাকরি পেতে, সরকারি চাকরি পেতে হলে তাদের বিসিএস পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। এই উদ্ভট ১৩ পরীক্ষাটি পাশ করা আর সবার সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক হলেও ডাক্তারদের জন্য ছিল না। নিয়ম চালু হয়েছে নতুন। খবর পাই যে আমরা যারা সরকারি চাকরি করছি, তাদেরও নাকি পরীক্ষাটি পাশ করতে হবে। কি কারণ? আমাদের তো চাকরি পাওয়ার কিছু নেই, আমরা তো সেই কবেই পেয়ে বসে আছি। কিন্তু সরকারি নতুন নিয়ম হল, পেয়েছি বটে চাকরি তবে পরীক্ষাটি পাশ করতে হবে চাকরিটি স্থায়ী করার জন্য। সরকারি চাকরি আবার অস্থায়ী হয়, এমন কথা শুনিনি কোনওদিন। এতকাল জানতাম সরকারি চাকরি মানেই স্থায়ী চাকরি। খবরটি শুনে শিপ্রা উদ্বিগ্ন। মোটা একটি বিসিএস গাইড কিনে সে মুখস্ত করতে শুরু করে দিল। আমারও একটি গাইড জোটে বটে কিন্তু পাতা ওল্টানো হয় না। পঞ্চম শ্রেণীর বালিকাদের মত গরুর রচনা লেখা আর ভাব সম্প্রসারণ করার কোনও ইচ্ছে হয় না আমার। বিসিএস ব্যপারটি বাংলা ইংরেজি অংক ইতিহাস ভুগোল থেকে শুরু করে গার্হস্থ বিজ্ঞান সাধারণ জ্ঞান সবকিছুর খিচুড়ি। আমি ডাক্তারি করব, ডাক্তারি ভাল জানলেই তো হল, আমার ওই খিচুড়ি জানতে হবে কেন! সরকার আর ডাক্তারদের চাকরি দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, তাই চাকরি যেন কম দেওয়া যায় তাই এই ব্যবস্থা। বিসিএস যারা পাশ করবে, তাদের জন্যও চাকরির ব্যবস্থা না করতে পারলে মনে হয় চারশ মিটার দৌড়ের একটি আয়োজন করবে সরকার, যে জিতবে তাকেই দেওয়া হবে সরকারি চাকরি। ভাব দেখে মনে হয় যে ডাক্তারে ভরে গেছে দেশ, কোথাও জায়গা নেই আর ডাক্তার বসানোর। বলা হচ্ছে সরকারের তহবিলে অত টাকা নেই যে চাকরি দেবে। ডাক্তারদের চাকরি দিতে পারছে না সরকার, অথচ দেশে কয়েক হাজার মানুষের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার।
শিপ্রা আর আমি ঢাকায় গিয়ে বিসিএস নামক পরীক্ষাটি দিয়ে আসি। গরুর রচনা না লিখলেও ছাগলের রচনা লিখতে হয়েছে। সরল অসরল সব রকম অংক কষে তরল করে, কাজী নজরুল ইসলাম কোন সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তা বানিয়ে দিয়ে, গোয়ালা ৫ সের দুধে ২ সের পানি মিশাইলে ২৮ সের দুধে কয় সের পানি মিশাইয়াছের উত্তরে তিন বালতি আর বৈকাল হৃদ কোথায় অবস্থিতর উত্তরে বগুড়া বসিয়ে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে আমরা আমাদের চাকরি স্থায়ী করি। এই পরীক্ষা পাশে চাকরির কোনও হেরফের হয় না, যেমন ছিল তেমনই থাকে। যারা বিসিএস পরীক্ষায় ফেল করে বসে আছে, তাদের চাকরিতেও কোনও চিড় ধরে না।
শিপ্রার জীবনে এরপর দুটি ঘটনা ঘটে। একটি হল বোম্বাই কলোনি থেকে সে আর তার মা চলে যায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোয়ার্টারে। দ্বিতীয়টি হল শিপ্রা প্রেমে পড়ে। প্রেমের পড়ার ব্যপারটি শিপ্রার জীবনে খুব উল্লেখযোগ্য। কারণ জীবনে সে প্রথম প্রেমে পড়েছে। মানু নামের এক ডাক্তার ছেলের প্রেমে পড়েছে সে। মানু বিবাহিত। শিপ্রাও বিবাহিত। শিপ্রার স্বামী থাকে মস্কোয়। ডাক্তারি পাশ করার পর শিপ্রা যখন দেখল যে ক্লাসের মেয়েরা ফটাফট সব ডাক্তার ছেলেদের বিয়ে করছে তখন সে যথারীতি খুব উদ্বিগ্ন। সকলে যখন বিয়ে করছে তখন বিয়ে ব্যপারটি নিশ্চয়ই মন্দ কোনও ব্যপার নয়, তারও নিশ্চয়ই তবে বিয়ে করা উচিত। কিন্তু বিয়ে করার জন্য পাত্র কোথায় পাবে সে! আশে পাশের কোনও ডাক্তারকে তার পছন্দ হয় না, এর এই মন্দ তো ওর ওই মন্দ। কাউকে যদিই বা পছন্দ হয়, তার সম্পর্কে সে অন্যদের কাছে জানতে চায়, অন্যরা ঠোঁট উল্টো দুএকটি কথা বললেই শিপ্রা চুপসে যায়। এরপর আমাকেই একদিন কণ্ঠে বড় উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কী করি বলো তো! বিয়ে করার কাউকে তো পাচ্ছি না। আমি বলেছিলাম, বিয়ে তোমার এক্ষুনি করতে হবে কেন! অনেকে আছে এখনও বিয়ে করেনি।
এ কথা শিপ্রাকে কদিন শান্ত রেখেছিল। এরপর শুনলো ক্লাসের কুৎসিত দেখতে কিছু মেয়েও বিয়ে করে ফেলেছে। এখন উপায় কি হবে! আমি কজন সুন্দরী মেয়ের উদাহরণ দিয়ে বললাম, ওরা তো এখনও করেনি। সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে হালিদার কথা বিশেষ করে বললাম।
শিপ্রা বলল, হালিদার কথা বাদ দাও। হালিদা তো জীবনে বিয়ে করবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এরপর শিপ্রা ভাবনা চিন্তা করে খুঁজে পেল তার এক খালাতো ভাই আছে বিয়ের বয়সী। যেই ভাবা সেই কাজ, খালাতো ভাইটি কোথায় আছে খবর নাও। খবর নিয়ে জানা গেল খালাতো ভাইটি মস্কোতে আছে, মস্কোতে সে দাঁতের ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিল, ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে। শিপ্রা এবার বলতে শুরু করল, আচ্ছ! বল তো এই হুমায়ুনকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়! বলব আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।
আমি বললাম, তাকে সেই ছোটবেলায় দেখেছো, এখন কি মিলবে তোমার মনের সঙ্গে? দেখ ভেবে।
শিপ্রা ভাবতে বসল। হুমায়ুন মস্কোয় মানুষের ডাক্তার না হলেও মানুষের দাঁতের ডাক্তার হয়েছে, এ আর এমন কি খারাপ! সাধারণত মানুষের ডাক্তাররা গরুর ডাক্তার, দাঁতের ডাক্তার এসব হাবিজাবি ডাক্তারদের পাত্তা দেয় না। কিন্তু শিপ্রা এমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত সে হুমায়ুনকে মস্কোতে একটি চিঠি পাঠিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কোনও কথা নয়, একেবারে সরাসরি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। হুমায়ুন কোনও এক কালে উলুঝুলু চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে, সেটিকে সম্বল করেই শিপ্রার এই আবেদন। হুমায়ুন রাজি হওয়ার পর শিপ্রা আর দেরি করেনি, সোজা উড়ে গেছে মস্কোয়, ওখানে বিয়ে করে মাস দুয়েক স্বামীর হোস্টেলে কাটিয়ে পেটে বাচ্চার ভ্রুণ নিয়ে দেশে ফিরেছে। শিপ্রার বাচ্চা হয় জোবায়েদ হোসেনের হাতে। বাচ্চাটি দেখে তিনি বলেছিলেন, হাতির পেট থেকে মুষিক বেরিয়েছে রে। মুষিকের নাম শিপ্রা রাখে আনন্দ। আনন্দ তার নানির যত্নে বড় হচ্ছে। শিপ্রা চাকরি করছে, মানুর সঙ্গে প্রতিদিনই তার দেখা হচ্ছে। মানুরও একটি ছেলে আছে, নাম হৃদয়। মানুর মত লোক ছেলের নাম হৃদয় রাখতে পারে, খানিকটা আশ্চর্যই হয়েছিলাম। মানুর মুখখানা সুন্দর হলেও, শরীরখানা মেদহীন হলেও, কথা বলতে গিয়ে ময়মনসিংহি আঞ্চলিকতার বাইরে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারে না, শিপ্রা বলছে যেতে হবে, মানু বলছে যাইতে অইব। শিপ্রার সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহ থাকলেও মানুর সামান্যতমও নেই। লম্বায় শিপ্রার চেয়ে দু ইঞ্চি খাটো খাঁটি ময়মনসিংহি গাট্টাগোট্টা কালচে মানু যখন ঝড়ের বেগে মোটরসাইকেলে শহর চষে বেড়ায়, দেখে যে কেউ বলবে ডাক্তার না হয়ে পাড়ার মাস্তান হলে তাকে মানাত বেশি। মানুর কোটরে আর কিছু নয়, পরিস্কার দুটো গরুর চোখ। এমন চোখ ছেলেদের মুখে ঠিক মানায় না। মানায় না বলেই মানুর ইস্পাতি শরীরটির কাঠিন্য চোখদুটোই আড়াল করে রাখে। শিপ্রা ভুলেই গেছে স্বামী বলে একটি বস্তু তার আছে, বস্তুটি একদিন মস্কো থেকে ফিরে আসবে দেশে, বস্তুটি তাকে আর তার ছেলে আনন্দকে নিয়ে একটি সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে ফিরবে। হুমায়ুনের স্বপ্ন নিয়ে শিপ্রা মোটেও উদ্বিগ্ন নয় বস্তু নিয়ে, উদ্বিগ্ন মানুকে নিয়ে। মানু তাকে সত্যি ভালবাসে তো! আমার কাছে জানতে চায় কী মনে হয় আমার, মানু তাকে ভালবাসে কি না। আমি কি করে বলব, মানুর মনে কি আছে। তখন একবার কেবল দেখেছি তাকে, শিপ্রা পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছে, মানু তাকে থামিয়ে উনারে চিনি ত! বলে আমার দিকে তেরচা চোখে সব জানি ভঙ্গিতে তাকিয়ে ডাক্তার রজব আলী ত আপনের বাবা বলে দৃষ্টিটি আমার মুখ থেকে সরিয়ে শিপ্রার মুখে মুহূর্তের জন্য ফেলে, তা থেকেও আবার সরিয়ে হাতের একটি কাগজে ফেলল। কাগজটি জরুরি কোনও কাগজ নয়, কিন্তু মানুর কাছে তখন খুবই জরুরি। শিপ্রার মুখে সেদিন মিষ্টি মিষ্টি হাসি আর মানুর মুখে বিন্দু বিন্দু ব্যস্ততার ঘাম। ঘাম মুছে ফেললেই হত, মানু মুছে ফেলেনি। আমি খুব নিশ্চিত হতে পারিনি মানুর আদৌ কোনও দুর্বলতা আছে কি না শিপ্রার জন্য। শিপ্রার এই মানু-প্রেম গড়িয়ে গড়িয়ে আপিসের অঙ্গন ছাড়িয়ে যায়। অবকাশের ধূলির ওপর শিপ্রার পদধূলির আস্তর জমে ওঠে। দীর্ঘক্ষণ মানুর লাল মোটর সাইকেলের দাঁড়িয়ে থাকায় অবকাশের মাঠের ঘাস জন্মের মত মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। বৈঠকঘরে বসে তারা সময় কাটাতে থাকে কথা বলে, তর্ক করে, অভিমান করে, রাগ করে, হেসে, কেঁদে, ঠাট্টা করে, চিমটি কেটে, কালপরশুর জন্য প্ল্যান করে। একসময় আমার বৈঠকঘর তাদের জন্য মোটেও প্রয়োজন হল না। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় শিপ্রার বাড়ির মাঠেই মানুর মোটর সাইকেল থামতে থামতে ওখানের ঘাসগুলোকে চিড়ে চ্যাপ্টা করে, হলুদ করে, মেরে, মাটির তলায় ডুবিয়ে দিতে থাকে। মানুর সঙ্গে তখন আর খুনসুটি নয়, রীতিমত বিছানায় গড়াগড়ি যায় শিপ্রা। গভীর রাতে মানু বাড়ি ফিরে যায়। শিপ্রার মা পাশের ঘরে বসে শব্দ শোনেন সবকিছুর, মোটর সাইকেল আসার যাওয়ার, শিৎকারের চিৎকারের। কিন্তু মেয়ের জীবনে তিনি নাক গলাতে পছন্দ করেন না। মেয়ে তাকে বলে দিয়েছে, ওই হুমায়ুনের সঙ্গে শোয়া আর না শোয়া সমান কথা, ও লোক মোটেও তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। শিপ্রা আমাকে নিখুঁত বর্ণনা করেছে বিছানায় হুমায়ুনের ভূমিকা — উঠল, কী করল সে নিজেই জানে, নেমে পড়ল। শিপ্রা তার শরীর খানা আর হুমায়ুনের জন্য খরচ করতে চায় না।
হুমায়ুন পাকাপাকিভাবে দেশে ফেরার পরও মানু গিয়েছে শিপ্রার বাড়িতে, স্বামীর সামনেই শিপ্রা মানুর সঙ্গে ঘন হয়ে বসেছে, ফিসফিস করেছে, ঢলে পড়েছে মানুর শরীরে হাসতে হাসতে। সে পারে না নিজের আবেগের আগুন কোনও কিছু দিয়ে চাপা রাখতে। দাউ দাউ করে যার তার সামনে লাল জিভ বেরিয়ে আসে। হুমায়ুনের সঙ্গে রাতে সে ভাই বোনের মত পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোয়, শরীরে হুমায়ুনের হাত তো নয় হাতের ছায়া পড়ার আগেই শিপ্রা বলে ওঠে, বিরক্ত কোরো না তো!
হুমায়ুন রাজশাহীতে চলে গেল দাঁতের একটি ক্লিনিক তৈরি করতে। হুমায়ুনের কি হবে না হবে তার কিছুই না ভেবে শিপ্রা মানুর জন্য দিন দিন উন্মাদ হয়ে ওঠে। মানু শিপ্রাকে বলেছে যে তার বউকে সে তালাক দিয়ে শিপ্রাকে বিয়ে করবে। শিপ্রা বিশ্বাস করেছে সব। শিপ্রা জানে না যে মানুর সঙ্গে তার সাদামাটা ধার্মিক ডাক্তার বউ শিরিনএর খুব ভাল সম্পর্ক, আনু নামের এক ডাক্তারকে সে অনেকটা রক্ষিতা হিসেবে রেখেছে এবং শিপ্রাকে সে ব্যবহার করছে প্রেমিকা হিসেবে। মানু প্রতিদিন তিন রমণীকে ভোগ করে যাচ্ছে, এবং তিনজনকেই সে তিন রকম ভাবে ভালবাসার কথা শোনাচ্ছে। শিপ্রা জানে না যে মানু আসলে কাউকেই ভালবাসে না, ভালবাসে কেবল নিজেকে।
মানুর এই চরিত্রের কথা আমি জেনেছি ইয়াসমিনের কাছ থেকে। ইয়াসমিনের জেনেছে তার সহপাঠী বন্ধু মিলনের কাছ থেকে, মিলন মানুরই আপন ছোট ভাই। এর চেয়ে ভাল আর কী প্রমাণ থাকতে পারে।
শিপ্রাকে আমি বলেছি, ‘দেখ এত উন্মাদ হয়ো না, মানু শুধু তোমাকে ভোগ করতে চায়, তোমাকে সে ভালবাসে না।’
‘কিন্তু মানু তো আমাকে বলেছে যে সে আমাকে ভালবাসে।’
‘মিথ্যে বলেছে।’
শিপ্রা মিথ্যে বলে না, তাই সে ভেবেছে অন্যরাও বুঝি মিথ্যে বলে না।
‘তোমার সঙ্গে শুয়ে সে আনুর বাড়িতে আনুর সঙ্গে শুতে যায়, তারপর আনুর বাড়ি থেকে এসে শিরিনের সঙ্গে শোয়।’
‘মানু আমাকে বলেছে, এক আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া আর কারও সঙ্গে তার এই সম্পর্ক নেই।’
এরপর শিপ্রা উঠে পড়ে লাগে সত্যতা যাচাই করতে। মানু এদিকে কোরান শরীফ মাথায় নিয়ে কসম কেটে বলছে আনুর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই, আনুর ছায়া মাড়ায় না মানু, কথা বলা তো দূরের কথা। শিপ্রা কোরানে বিশ্বাস না করলেও মানু করে। কোরানে বিশ্বাস করা লোক কোরান নিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারে না, শিপ্রার ধারণা। কিন্তু একদিন শিপ্রা একটি অদ্ভুত কাজ করে। সে তার গায়ে একটি কালো বোরখা চাপিয়ে, বাসে করে মুক্তাগাছায় গিয়ে, মুক্তাগাছা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, যেখানে মানু আর আনু দুজনেই চাকরি করে, ঢোকে। রোগীদের কাতারে দাঁড়িয়ে থাকে রোগীর মত। বোরখার আড়াল থেকে লক্ষ্য করে মানু আর আনুকে। মানু আর আনু দুজনে গল্প করছে, হাসছে । শুধু দেখাই তার উদ্দেশ্য ছিল না, দেখা দেওয়াও ছিল উদ্দেশ্য। হঠাৎ মানু আর আনুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে শিপ্রা বোরখার মুখটি চকিতে খুলে ফেলে। মানু ভূত দেখার মত চমকে ওঠে। দুজনকে হাতে নাতে ধরার পরই শিপ্রার সঙ্গে মানুর সম্পর্ক শেষ হতে পারতো কিন্তু হয় না। মানু ক্ষমা টমা চেয়ে কেঁদে কেটে একাকার করে শিপ্রাকে আবার বশে আনে।
যে শিপ্রা হিসেব করে জীবন চলত, যে শিপ্রা যে কোনও কিছুতেই উদ্বিগ্ন হত, সেই শিপ্রা কী ভীষণ রকম পাল্টো গেছে! আমাদের বয়সী ডাক্তাররা এফসিপিএসএ ভর্তি হবার জন্য দিন রাত পড়াশোনা করছে জেনেও শিপ্রা কোনও আগ্রহ দেখায় না এফসিপিএসএর জন্য। তার নাওয়া খাওয়া সব গোল্লায় গেছে। শরীর শুকোচ্ছে। সুন্দর মুখটিতে কালো কালো দাগ পড়ছে। যে শিপ্রা প্রাণখুলে হাসতো, অন্যদের হাসাতো, যার রসবোধ ছিল অতুলনীয়, সেই শিপ্রা শুকনো মুখে বসে থাকে মরা গুঁড়ির মত, শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে রং ওঠা দেয়ালের দিকে। মানুর জন্য পাগলের মত কাঁদে সে। যার আত্মমর্যাদা বোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর, সে ই কি না নিজেকে অপমানিত হতে দিচ্ছে একটা অসৎ অর্থলোভীর কাছে। মানু এর মধ্যেই নদীর পাড়ে একটি চেম্বার খুলে বসেছে, রিক্সাঅলা-দালালদের দিয়ে গুদারাঘাটে গ্রাম থেকে শহরে ডাক্তার দেখাতে আসা রোগী ধরে আনে। খামোকা রোগীর মল মুত্র রক্ত পরীক্ষা করার নাম করে রোগীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা খসিয়ে নেয়। শিপ্রা দেখে সব, দেখেও তার চক্ষু বুজে থাকে। তার চলাফেরা নিয়ে কে কি বলল না বলল এ নিয়েও তার কোনও উদ্বেগ নেই। সে যে করেই হোক, যা কিছুর বিনিময়েই হোক, মানুকে চায়। মানু শিরিনকে আজ তালাক দেবে, কাল দেবে করে করে বছর চলে যাচ্ছে তালাক দিচ্ছে না। শিপ্রা কি বোঝে না এসব! বোঝে না যে মানু তাকে ধোঁকা দিচ্ছে! আসলে সে কোনওদিনই ওই গর্দভ বউটিকে তালাক দেবে না! শিপ্রার এই বোধবুদ্ধিহীন প্রেমটি দেখলে আমার বড় বিরক্তি ধরে।
একদিন শিপ্রা আমার বাড়ি এসে অনেকক্ষণ বসে থাকে। অনেকক্ষণ কাঁদে, একসময় দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলে, ‘জীবনে আমি অন্তত একবার অরগাজমের স্বাদ পেতে চাই।’ আমি তো অবাক, ‘বল কি! তুমি অরগাজম পাওনি আজও?’
শিপ্রা বলল সে পায়নি। হুমায়ুনের কাছ থেকে তো প্রশ্ন ওঠে না। মানু যেহেতু সঙ্গমে পটু, দীর্ঘক্ষণ, চাইলে দুঘন্টাও চালিয়ে যেতে পারে, মানুর পক্ষেই হয়ত সম্ভব তাকে অরগাজম দেওয়া।
শিপ্রার ওপর আমার রাগ হয় আবার মায়াও হয়।
অরগাজম নিয়ে এরপর আমি একটি জরিপ চালিয়ে দেখেছি বেশির ভাই মেয়েই জানে না জিনিসটি কী। শিপ্রা কোনওদিন এটি না পেলেও জানে অরগাজম বলে একটি ব্যপার আছে. তাই সে এটি পেতে চায়। যারা জানে না এটি কি জিনিস, তারা তো কোনওদিন এটি চায়ও না।
আমার জীবন কেবল শিপ্রার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ নিয়ে কাটে না। নিজের ডাক্তারি বিদ্যেটি কাজে লাগানোর জন্য আমি যত রকম চেষ্টা করা যায়, করতে থাকি। নাম ডিগ্রি লিখে রোগী দেখার সময় উল্লেখ করে একটি সাইনবোর্ড লিখিয়ে অবকাশের কালো ফটকে টানিয়ে দিই। জমান প্রিন্টার্স থেকে ডাক্তার লেখা প্যাড করেও নিয়ে আসি। সবই হয়। রোগীও আসতে শুরু করে। কিন্তু পাড়ার রোগী, চেনা মুখ। যখনই ওরা ডাক্তারের ফি দিতে যায়, লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে যায়। কান যেন লাল না হয়, কানের রং যেমন আছে, তেমন যেন থাকে তার জন্য চেষ্টা করেছি, তারপরও লাল হওয়া কমেনি। পাড়ার লোকের কাছ থেকে টাকা নিতে হাত ওঠে না, প্রেসক্রিপশান লিখে হাত টেবিলের তলায় গুটিয়ে রাখি। এরপর আরও একটি শখ হয় আমার। শখটি একটি ক্লিনিক করার। বেদনা নাশক ব্যবহার করে প্রসূতিদের সন্তান প্রসব করানোর জন্য অবকাশের সামনের ঘরটিকে ছোটখাটো একটি ক্লিনিক করার স্বপ্ন নিয়ে বাড়ির উঠোনে একটি পড়ে থাকা বড় একটি টিন ধুয়ে মুছে রং করিয়ে ডাক্তার তসলিমা নাসরিন, এম বি বি এস, বি এইচ এস(আপার), স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, এখানে বেদনা নাশক ব্যবহার করে বাচ্চা ডেলিভারি করা হয় ইত্যাদি লিখিয়ে আনি গোলপুকুর পাড়ে জয়ন্ত তালুকদারের দোকান শিল্পশ্রী থেকে। যেদিন সাইনবোর্ডটি অবকাশের সামনে টাঙালাম, সেদিনই বাবা এটি খুলে বারান্দায় এনে রেখে বললেন ক্লিনিক শুরু করতে গেলে লাইসেন্স লাগে, যেখানে সেখানে ক্লিনিক বসিয়ে দিলেই হয় না। ডাক্তারি করার জন্য আমার অতি-উৎসাহ দেখে বাবা নিজেই আমাকে একটি চাকরি দিলেন, চাকরি পেয়ে আমি মহাখুশি। তাঁর চেম্বারের বারান্দায় ছোট একটি ঘর বানিয়ে একটি প্যাথলজি ক্লিনিক দিয়েছেন, টেবিলে মাইক্রোসকোপ, তাকে লাল নীল শিশি সাজানো। বিকেলে সেখানে বসব। তিনি তার রোগীদের মলমুত্রকফথুতু পাঠাবেন আমার কাছে, আমি পরীক্ষা করে দেব। কুড়ি টাকা করে পাবো প্রতি পরীক্ষায়। এসময় বাবার সঙ্গে আমার বেশ সখ্য গড়ে ওঠে। রাতে বাড়ি ফিরে বাবা আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দাবা খেলতে বসেন, অবশ্য আমাকে হারিয়ে দিতে তাঁর খুব বেশি সময় কখনও লাগে না। সে এক দেখার বিষয় হয় আমাদের দাবা খেলা। বাড়ির সকলে আমার পক্ষে, বাবার পক্ষে কেবল এক বাবাই। মা খুব চান আমি যেন বাবাকে হারিয়ে দিই। বাবা আমার ঘোড়া খেয়ে নিলেন তো মা অস্থির হয়ে বলতে থাকেন, ইস, ঘোড়াটা আগেই সরাইয়া ফেলতা, দেখ না তোমার বাবা কেমনে চিন্তা কইরা খেলে। তুমি চিন্তা ছাড়াই গুটি সরাও কেন? আমি হারলে আমি আর কত, আমার চেয়ে অনেক বেশি নিরানন্দে ভোগেন মা। বাবার প্যাথলজিতে গিয়ে মলমুত্র পরীক্ষায় একসময় ভাটা পড়ে যখন পপুলার ক্লিনিক থেকে কল আসা শুরু হয়। পুপুলার ক্লিনিকটি সি কে ঘোষ রোডে, দাদার বাচুপান কা দোস্ত জাহাঙ্গীর ক্লিনিকের মালিক। ওখানে ডাক্তারি ভাষার মেনস্ট্রুয়েশন রেগুলেশন, সংক্ষেপে এমআর, সাধারণের ভাষায় এবরশান করাতে আসে মেয়েরা, তাদের জন্যই আমার ডাকা। প্রতি এমআরে তিনশ টাকা দেওয়া হয় আমাকে। বাকি এক হাজার বা বারোশ টাকা ক্লিনিক নিয়ে নেয়। এম আর এ আমার হাত মোটেও পাকা ছিল না। এ বিষয়টি ডাক্তারি শাস্ত্রের তেমন কোনও জরুরি বিষয় নয়। একটি মোটা মত সিরিঞ্জে উল্টো চাপ দিয়ে জরায়ুর ভেতরের ভ্রূণ বের করে নিয়ে আসতে হয়। অপারেশন থিয়েটারে নার্সরাই রোগীকে টেবিলে শুইয়ে তৈরি করে রাখে, আমাকে শুধু গিয়ে হাতে গ্লবস পরে ব্যপারটি সারতে হয়। প্রথম প্রথম দুএকজন রোগীর জরায়ু পরিষ্কার হয়নি, ইনফেকশনে ভুগেছে, আবার ফেরত গেছে ভেতরের রয়ে যাওয়া জিনিস বের করতে। ওই দুএকটি দুর্ঘটনা দেখে আমি মরমে মরেছি। ধীরে ধীরে হাত পেকে যায় এমআরে। ছায়াবাণী সিনেমার কাছে সেবা নার্সিং হোমেও আমার ডাক পড়ে এমআর করার জন্য। বাড়তি টাকা উপার্জন হচ্ছে বেশ। বাবা ডাক্তারি ব্যপার নিয়ে আমার আগ্রহ উসকে দেন তবে ছোটখাটো চাকরি আর খুচরো কিছু এবরশান নিয়ে আমার পড়ে থাকা তিনি চান না, চান আমি পড়াশোনা করি। এফসিপিএস ডিগ্রি নিই। এফসিপিএস না পাশ করলে এমবিবিএস দিয়ে কাজের কাজ কিμছু হবে না। চিরকাল গাঁওগেরামের ডাক্তার হয়ে থাকতে হবে। এমবিবিএস আজকাল অলিতে গলিতে পাওয়া যায়। সত্যিকার ডাক্তারি করতে চাইলে এক্ষুনি যেন আদা জল খেয়ে যেন বই নিয়ে বসে পড়ি এফসিপিএসে ভর্তি হওয়ার জন্য। বই নিয়ে আমার বসা হয়, তবে ডাক্তারি বই নয়, কবিতার বই নিয়ে। বাবা প্রতিদিনই আমার ক্লাসের কোন কোন ছেলে মেয়ে পিজিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশান করতে গেছে তার খবর নিয়ে আসেন আর আমার জন্য হা হুতাশ করেন। আমার শখের ডাক্তারি করার ইচ্ছেকে তিনি প্রথম প্রথম আসকারা দিলেও অথবা বাধা না দিলেও, বাধা না দেওয়াই আমাদের কাছে একরকম আসকারা, অপছন্দ করা শুরু করলেন। পপুলার ক্লিনিক আর সেবা নার্সিং থেকে যে তিনশ টাকা করে আয় করি, ও নিয়েও একদিন ভেঙচি কাটেন, হু, এফসিপিএস পাশ করলে একটা অপারেশন কইরাই তিন লাখ টাকা পাইতি। বাবা নিজের কথা বলেন, তিনি একটি গরিব কৃষকের ছেলে হয়ে কৃষক না হয়ে ডাক্তার হয়েছেন। তিনি এমবিবিএস ডাক্তার, তাঁর সন্তান কেন এমবিবিএসে পড়ে থাকবে! সে এফসিপিএস ডাক্তার হবে, বিদেশে গিয়ে এফআরসিএস এফআরসিপি ডিগ্রি নিয়ে আসবে। পড়াশোনার এমন সুযোগ আমি নষ্ট করছি খামোকা, এ তিনি মেনে নিতে পারেন না। যে সময় যাচ্ছে, সে সময় আর যে ফিরে আসবে না, যে সুযোগ আমি নষ্ট করছি, সে সুযোগ যে আমি আর পাবো না তা তিনি দিনে দশবার করে বলতে থাকেন।
বাবা যাই বলুন না কেন, এফসিপিএস এর জন্য পড়াশোনা আমার হয়ে ওঠে না। খুচরো ডাক্তারিতেই সময় কাটতে থাকে। কিন্তু এই ডাক্তারি নিয়েও দীর্ঘদিন মেতে থেকে একসময় দেখি আমি হাঁপিয়ে উঠছি, আমি অন্য কিছু একটা করতে চাই। সেই অন্য কিছুটা একদিন করে বসি। সকাল কবিতা পরিষদ নামে একটি সংগঠন করি। কবিতা পরিষদের কার্যালয় অবকাশের সামনের ঘরটি, যে ঘরটিতে একটি ক্লিনিক করার ইচ্ছে ছিল আমার।
০৩. জীবনগুলো
জীবন আমার দুটো শহরে ভাগ হয়ে যায়। ময়মনসিংহে বাড়ি, আত্মীয় স্বজন, চাকরি। ঢাকায় সাহিত্য, সংস্কৃতি, বন্ধুবান্ধব। ঢাকা আমাকে টানে খুব। হাতে টাকা হলেই বাসে নয়ত ট্রেনে চড়ি। ঢাকা যাওয়ার আরও একটি নতুন কারণ হল সুহৃদ। সুহৃদ এখন ঢাকায়। সুহদকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ব্যপার ছিল না। ছোটদা এসে ওকে ধরে বেঁধে কাঁদিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন একবার, ঢাকার ইশকুলে ভর্তি করাবেন বলে। মাও বলেছিলেন, তিনি আর কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। এরপর মা নিজেই ঢাকায় গিয়ে ছোটদা আর গীতার হাতে পায়ে ধরে ঘরের ছেলেকে ঘরে নিয়ে এলেন, অবশ্য হাতে পায়ে ধরার দরকার ছিল না, গীতা এমনিতেই ছেলেকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। ওর আচরণ দেখে গীতা আকাশ থেকে পড়ে। এ ছেলে তার নিজের, এ ছেলেকে সে গর্ভে ধারণ করেছে দীর্ঘ নমাস, তার গর্ভ থেকেই গড়িয়ে নেমেছে ছেলে, নাড়ির বন্ধন যদি থাকে কারও সঙ্গে, তা তার সঙ্গেই আছে, কিন্তু সে ডাকলে ছেলে কাছে আসবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে তার কোলে, তা নয়ত দৌড়ে পালায়। চলে যায় ওর দাদুর কোলে নয়ত ফুপুদের কাছে। এত সাহস এই ছেলে পেল কোত্থেকে, গীতা বুঝে পায় না। রেগে গা আগুন করে বসে থাকে, গা থেকে ধোঁয়া বেরোয়। সেই ধোঁয়ার ভেতর থেকে গীতা চিৎকার করতে থাকে, ‘তোমার গুষ্ঠির মধ্যে পইড়া আমার ছেলে নষ্ট হইয়া গেছে। তাগর যদি এত ছেলে দরকার থাকে, তাইলে তারা বিয়াইয়া লউক একটা। গীতার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ছোটদা বলতে থাকেন, গীতা ও গীতা, আমি তোমার ছেলেকে তোমার কাছে যেমনেই হোক আইন্যা দিতাছি।’ এরকম শপথে গীতার মন ভরে না, ছোটদা তার মন ভরানোর জন্য বলেন যে সব দোষ তাঁর, তাঁর দোষেই আজ গীতাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে, তাঁর উচিত ছিল না ছেলেকে জন্মের পর অবকাশে পাঠানো, তাঁর দোষেই আজ গীতার নিজের ছেলে আজ গীতার কাছ ঘেঁসতে চায় না। তাঁকে আরও বলতে হয় যে তাঁর মা আর তাঁর দু বোনের কারণে সুহৃদ নষ্ট হয়ে গেছে, ওকে মানুষ করতে হলে এখন গীতা ছাড়া গতি নেই। গীতা শোনে। চিৎকার আপাতত থামিয়ে সে ওঠে, ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে সে ছোটদাকে ঘর থেকে বের করে শব্দ করে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে টাকা পয়সা গয়নাগাটি আর শাড়িতে ঠাসা আলমারি খুলে ইস্ত্রি করা সুতির শাড়িগুলোর কিনার দিয়ে হাত ঢুকিয়ে সুহৃদের ছবির অ্যালবাম বের করে অবকাশে আমাাদের সঙ্গে তোলা ওর সব ছবি ছিঁড়ে টুকরো করে, আস্ত রাখে কেবল তার সঙ্গে সুহৃদের ছবিগুলো।
সুহৃদকে নিয়ে অবকাশে আমাদের আবেগ আর উচ্ছঅ!সের শেষ নেই। কদিন পর পরই ওর ছবি তোলা হয়, ইয়াসমিন তার এক বান্ধবীর ভাইয়ের খোঁজ পেয়েছে, যার স্টুডিওর দোকান আছে, সেই ভাইয়ের ক্যামেরা এনে প্রচুর ছবি তুলে যেদিন নিয়ে এল ছবিগুলো, হুমড়ি খেয়ে একেকজন দেখতে থাকি, গীতা সেদিনই ছোটদাকে নিয়ে আসে ময়মনসিংহ, ছবিগুলো আমাদের মত অত উৎসাহ নিয়ে দেখে না, না দেখলেও উৎসাহ নিয়েই বলে, ছবিগুলো সব যেন তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। কারণ আমরা তো সুহৃদকে জলজ্যান্ত পাচ্ছি, সে যেহেতু পাচ্ছে না, ছবি দেখেই তার সাধ মেটাতে হবে। এ কথাটি ঠিক সে বলেও না, আমরাই অনুমান করে নিই। অনুমান করে সুহৃদের যত ছবি যেখানে ছিল, সবই তাকে উদার হস্তে দান করা হয়। এই দানে মার আহা আহা-ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বড়। সেই বিকেলেই ইয়াসমিনের বান্ধবী কৃষ্টি এলে ইয়াসমিন যখন সুহৃদের ছবিগুলো গীতার কাছে চায় কৃষ্টিকে দেখাবে বলে, গীতা মুখের ওপর বলে দেয়, না, ছবি এখন দেওয়া যাবে না, কেন যাবে না? যাবে না। কারণ কি? অসুবিধা আছে। কি অসুবিধা? আছে। কাউকেই ছবি দেখতে দেয়নি। ব্যাগে করে সে ঢাকা নিয়ে এসেছিল। তারপর এই তার ছিঁড়ে ফেলা। নিগেটিভগুলোও কেটে টুকরো করে রান্নাঘরের ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে রাখল। এতে তার মন আপাতত শান্ত হয়, কিন্তু হাতগুলো নিশপিশ করতে থাকে, হাতগুলোর ইচ্ছে করে নখের আঁচড়ে আমাকে, ইয়াসমিনকে আর মাকে রক্তাক্ত করতে। কী দোষ আমাদের! নিশ্চয়ই আমাদেরই দোষ, আমরা অন্যের বাচ্চাকে নিজের বাচ্চা বানিয়ে নিয়েছে, এই দোষ আমাদের। আদরে আহলাদে মানুষ হওয়া সুহৃদ এমনিতেই কারও ডাকে পেছন ফেরে না, মা যে কত ডাকেন সুহৃদ যখন দৌড়ে ছাদে বা মাঠে চলে যেতে থাকে, ভয়ে যে কখন আবার কোথাও পড়ে গিয়ে ব্যথা পায়, সুহৃদ ফেরে না। বাতাসের আগে আগে ছোটে সে, যখন ছোটে। কিন্তু গীতার প্রশ্ন সে তার ছেলেকে ডাকলে ছেলে তো শুনতে বাধ্য, কিন্তু ছেলে কেন শোনে না তার ডাক? কেন দাঁড়াতে বললে দাঁড়ায় না, বসতে বললে বসে না! সুহৃদের অবাধ্য আচরণ দেখে গীতা ভীষণ ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। পৃথিবীর আর কেউ ডাকলে সুহৃদ না ফিরুক, কিন্তু গীতা যখন ডাকে, তখন তো ওর জানা উচিত কে ওকে ডাকছে! ও কি জানে না গীতা কে! গীতা বিষম রোষে দাপায়, সুহৃদকে হাতের কাছে পেয়ে হ্যাঁচকা টেনে কাছে এনে চোখ রাঙিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলেছে, ‘আমি যে তোমার মা হই, তা জানো? আমি যে তোমার সবচেয়ে বেশি আপন, তা জানো? আমি ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে আসো না কেন? কারণ কি? এরপর আমি একবার ডাক দিলেই সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে আইসা দাড়াইবা, মনে থাকবে?’ সুহৃদ হতবাক দাঁড়িয়ে মনে থাকবের মাথা নেড়ে দৌড়ে গিয়ে মার আঁচলের তলে নিজেকে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ওর কান্না দেখে বুক ফেটে যায় আমাদের। মা প্রতিদিনই ওকে বলেন, নিজের বাবা মাকে যেন ও ভালবাসে। তবে গীতাকে যখন মা রিমঝিম সুরে বলতে নিচ্ছিলেন, ‘আদর কইরা কইলেই তো ছেলে বুঝে..।’ গীতা বজ্রপাত ঘটায়, ‘আমার ছেলেরে আদর কইরা বলি কি মাইরা বলব, সেইটা আমি বুঝব।’ মা চুপ হয়ে যান। আমরাও চুপ হয়ে বসে থাকি। অনেকক্ষণ চুপ থেকে মা বলেন, ‘ছেলে এইখানে থাকে বইলা আমাদের চেনে, আমাদের কাছে আসে, আমাদের প্রতি টান তার। তুমি যখন নিয়া যাইবা ওরে, তখন তোমার প্রতিও টান হইব। তখন তো তোমার কাছ থেইকা ও আমাদের কাছেই আসতে চাইব না।’ গীতা দুদিনের জন্য অবকাশে বেড়াতে এসে সুহৃদকে বশংবদ ভৃত্য বানানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকে। গীতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সুহৃদ ছটফট করে। এরপর ছোটদা আর গীতা যখনই সুহৃদকে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে, ও ভয়ে কেঁপে আমাদের আঁকড়ে ধরে কানে কানে বলেছে, ‘আমাকে কোথাও লুকাইয়া রাখো, আমাকে যেন না নিয়া যাইতে পারে।’ আমরা ওকে লুকিয়ে না রাখলে ও নিজেই লুকোনোর জায়গা খুঁজে খুঁজে টিনের ঘরের খাটের নিচে কাগজের বাক্সের মধ্যে নিজেকে সারাদিন লুকিয়ে রেখেছে। গীতা লক্ষ্য করে অবকাশের মানুষগুলোই সুহৃদের আপন এবং ঘনিষ্ঠ, সুহৃদ তাদেরই ভালবাসে, গীতার জন্য ওর কোনও ভালবাসা নেই। গীতা ওর কাছে মূর্তিমান রণচণ্ডী বিভীষিকা ছাড়া, ভয়ংকর ত্রাস ছাড়া কিছু নয়। সুহৃদকে টেনে হিঁচড়ে আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে গত কয়েক যাত্রা গীতা বলে আসছে, ‘এই দুনিয়ার কেউ তোর আপন না, আমি ছাড়া।’ সুহৃদ ফ্যালফ্যাল করে গীতার দিকে তাকিয়ে দৌড়ে পালাতে চায়, গীতা সাঁড়াশির মত ধরে রাখে ওর ঘাড়। কেঁদে ওঠে সুহৃদ, কান্না দেখে গীতার ইচ্ছে হয় বেয়াদব ছেলেটিকে খুন করতে।
সুহৃদকে নিয়ে কম টানা হেঁচড়া হয়নি। মাঠে ও ব্যাডমিন্টন খেলছিল, ছোটদা ঢাকা থেকে এসে কাউকে কিছু না বলে ওকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যান মাঠ থেকে। সুহৃদের আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও আর্তনাদে সারা পাড়া কাঁপছিল। এরপর কদিন পর ছোটদা এসে ওকে অবকাশে ফেরত দিয়ে যান। ধড়ে প্রাণ ফিরে পায় ছেলে। আমরা ওকে নতুন কুঁড়ি ইশকুলে ভর্তি করিয়ে দিই। ইশকুলে দিয়ে আসি, ইশকুল থেকে নিয়ে আসি। বাড়িতে মা ওকে এ বি সি ডি, ক খ গ ঘ শিখিয়ে, ছবি আঁকা শিখিয়ে, যুক্তাক্ষর শিখিয়ে, সুন্দর সুন্দর ছড়া শিখিয়ে ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্র করে তুললেন। আমাদের আদর আর ভালবাসার দোলায় সুহৃদ দুলতে থাকে। এরপর ওকে যে করেই হোক ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যেদিন ছোটদা আবার আসেন, যে করেই হোক নিয়ে তিনি যাবেনই, জগত উল্টো গেলেও নেবেন, সেদিন ইয়াসমিন সুহৃদকে নিয়ে পালায়। ফিরে আসে সন্ধের আগে আগে। ছোটদা সারাদিন অপেক্ষা করে ঢাকা চলে গেছেন। সুহৃদকে নষ্ট বানানোর জন্য আমাদের একশ ভাগ দায়ি করে হুমকি দিয়ে গেছেন, ওকে যদি কালই ঢাকায় না পাঠানো হয়, তবে এ বাড়ির সঙ্গে তার আার কোনও সম্পর্ক থাকবে না।
অবকাশে বৈঠক বসে। বাবার সিদ্ধান্ত, সুহৃদকে তার বাপ মার কাছে এখন দিয়ে দেওয়াই উচিত, ঢাকায় ভাল ইশকুল আছে, ওখানে লেখাপড়া করার সুযোগ ভাল পাবে। এই সিদ্ধান্তটি আমাদের বুক ছিঁড়ে টুকরো করে দেয়, কিন্তু সুহৃদের আলোকিত আগামীর কথা ভেবে টুকরোগুলো শিথিল আঙুলে জড়ো করি। ছোটদা আর গীতার পক্ষে ওকে ঢাকায় নেওয়া সম্ভব নয়, হাত পা মুখ সব চেপে গাড়িতে বসালেও সে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে ঝাঁপ দিতে চায় রাস্তায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয় সুহৃদকে আমি আর ইয়াসমিন ঢাকায় দিয়ে আসবো। ওর বাবা মার কাছে ওকে সমর্পণ করতে যাচ্ছি, এ কথা শুনলে ও যেহেতু কিছুতেই যেতে চাইবে না, ঢাকায় মেলা দেখতে যাবো, আজই ফিরে আসবো বিকেলে, এই মিথ্যে কথাটি বলে ওকে নিয়ে আমি আর ইয়াসমিন ভোরের ট্রেনে চড়ি। ঢাকায় কমলাপুর ইস্টিশনে নেমে একটি রিক্সা নিই। সুহৃদ চারদিকে তাকিয়ে মেলা খুঁজছে। রিক্সা যখন নয়াপল্টনের রাস্তায় এল, ও চিনে ফেলল রাস্তাা। হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার শুরু করল, আমরা মেলায় যাবো বলেছি, কিন্তু মেলায় না গিয়ে কেন এ রাস্তায় এসেছি! যত বলি যে ছোটদার সঙ্গে একবার দেখা করেই মেলায় যাবো, তত ও গলা ছেড়ে কাঁদে, ও যাবেই না ছোটদার বাড়িতে। নয়াপল্টনে থেমে সুহৃদকে আইসক্রিম খাইয়ে, গলিতে হেঁটে হেঁটে অনেকটা সময় নিয়ে মিথ্যে গল্প শোনাতে হল যে আমাদের হাতে টাকা নেই মেলায় যাওয়ার, ছোটদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তবে মেলায় যেতে হবে, ময়মনসিংহে ফিরতে হবে। আমাদের আদরে পোষা ছেলে আমাদের কথা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে ছোটদার বাড়িতে ঢোকে। বাড়িতে ছোটদা ছিলেন না, গীতা ছিল। গীতাকে দেখে সুহৃদ সেঁটে রইল আমাদের গায়ে, সুহৃদের সেঁটে থাকা গীতার সয় না, গীতা ওর মা হওয়ার পরও তার দিকে ও এক পা বাড়াচ্ছে না, এত বড় দুঃসাহস ওর হয় কী করে! সুহৃদকে শক্ত হাতে টেনে নিয়ে গীতা ঘাড় ধাককা দিয়ে মেঝেয় ফেলে দিলে আমরা দৌড়ে গিয়ে ওকে যেই তুলেছি, কেড়ে নিয়ে ওর গালে এক চড় কষিয়ে দিল। ব্যাকুল হয়ে ও আমাদের দিকে দৌড়ে আসতে গেল, গীতা ওর সার্টের কলার খামচে ধরে পেছনে টেনে নিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, ‘ওইদিকে যাস ক্যা? এইদিকে আয়। আমার অর্ডার ছাড়া এহন থেইকা কিছু করলে খুন কইরা ফালাইয়াম।’
সুহৃদ থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। আজ পর্যন্ত অবকাশে কেউ ওকে টোকা পর্যন্ত দেয়নি। চড় কাকে বলে সে জানতো না। ধাককা কাকে বলে জানতো না। এ ধরনের রুক্ষ ভাষা ওর প্রতি কাউকে ব্যবহার করতে কোনওদিন সে শোনেনি।
ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করলে গালে আবারও চড়। পিঠে কিল।
‘মুখ থেইকা একটাও যেন শব্দ বাইর না হয়।’ গীতার অর্ডার।
শব্দহীন আর্তনাদে সুহৃদের শরীর ফুলে ফুলে উঠছিল।
আমরা আড়ালে গিয়ে কাঁদছি। বলতে পারছি না কিছু। ক্ষীণ কণ্ঠে মুদু প্রতিবাদ করলেও গীতা তার শোধ নিচ্ছে সুহৃদকে মেরে। সুহৃদ এখন গীতার গণ্ডির ভেতর, গীতার যা ইচ্ছে, সে তাই করবে। সে যদি চায় তার ছেলেকে কুচি কুচি করে কাটতে, সে কাটবে। যে ছেলে রাজপুত্রের মত ছিল অবকাশে, যার যত্নে মা বাবা ইয়াসমিন আমি ব্যস্ত ছিলাম সারাক্ষণ, যাকে আদর আর ভালবাসার জলে ডুবিয়ে রেখেছি, যাকে মুখে তুলে দিনে আমরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় মুরগির সুপ, ফলের রস, খাঁটি গরুর দুধ, দুধের শর, মাছের কোপ্তা, গাজরের হালুয়া, ডিমের পুডিং ইত্যাদি পুষ্টিকর আর সুস্বাদু খাবার খাইয়েছি, সেই ছেলেকে সারাদিন খেতে দেয়নি গীতা।
আমাদের আর সহ্য হয়নি দৃশ্য দেখতে। আমরা সারা পথ চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ময়মনসিংহে ফিরেছি। পথে একটি প্রশ্নই আমার মনে জেগেছে, গীতা কি সত্যি সত্যিই চেয়েছিল সুহৃদ ফিরে যাক ঢাকায়! আমার মনে হতে থাকে গীতা চায়নি সুহৃদ যাক। ও দূরে থাকলেই গীতা সুখে ছিল। ছোটদাকে অপরাধবোধে ভুগিয়ে কেঁচো করে রাখার জন্য গীতার কাছে সুহৃদ ছিল একটি চমৎকার অস্ত্র।
গীতার দুর্ব্যবহারের পরও আমরা নয়াপল্টনে যাই সুহৃদকে দেখতে। সুহৃদ জীবন ফিরে পায় আমাদের দেখলে। কিন্তু আমাদের কাছে আসতে গেলেই গীতা ওকে ডেকে নিয়ে যায় অন্য ঘরে। ওকে অনুমতি দেওয়া হয় না আমাদের কারও কাছে আসার, আমাদের সঙ্গে বসে দুএকটি কথা বলার। ওকে বন্দি করে রাখা হয় অন্য ঘরটিতে, সেই ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ও দেখে আমাদের। গীতার অনুমতি নিয়ে ও যদি জল খেতে ওঠে বা পেচ্ছ!বখানায় যায়, তখন পলকের জন্য চোখাচোখি হয়, ওই চোখাচোখিতেই আমরা ভালবাসা বিনিময় করি। সুহৃদ ওঠে ওই পলকের দেখাটুকুর জন্যই। গীতার আচরণের প্রতিবাদ করব এমন সাহস আমাদেরও নেই। আমরাও মুখ বুজে থাকি বাঘে দৌড়োনো লুকোনো হরিণের মত।
গীতাকে নানা উপহারের উষ্ণতা দিয়ে গলিয়ে ওকে যদি সামান্য ক্ষণের জন্য দেখার অনুমতি পাই, আমাদের সামনে এসে ওর চোখ চিকচিক করে ওঠে খুশিতে। যে সুহৃদ প্রাণ খুলে হাসত, কাঁদত, যেমন ইচ্ছে তেমন চলতো, দৌড়োতো, কলকল করে কথা বলত —- সেই সুহৃদ এখন হাসতে পারে না, কাঁদতে পারে না, কথা মিনমিন করে বলে, প্রায় শব্দহীন স্বর, শঙ্কিত পদক্ষেপ, নিস্প্রভ, নিরুত্তেজ। একটি কথাই ও দ্রুত বলতে আসে, থাকো, যাইও না। হাতে যদি ট্রেনের টিকিট দেখে চলে যাবার, মুহূর্তে ওর চোখ জলে উপচে পড়ে, টিকিট কেড়ে নিতে চায়। ও বাড়িতে থাকব, ওর সঙ্গে দেখা হবে না, ও ঘরবন্দি থাকবে, তারপরও ওর স্বস্তি হয় যে আছি, বাড়ির কোনও না কোনও ঘরে আছি। সুহৃদের সারা মুখে ভয়, চোখদুটিতে ভয়। গীতার ভয়ে সে পাথর হয়ে থাকে। যে ছেলেটি বেলায় বেলায় খেতো, খেতে না চাইলেও গল্প বলে বলে নানা কৌশলে যাকে খাওয়ানো হত, সেই ছেলে ক্ষিধেয় মরে গেলেও কিছু খেতে পাওয়ার অনুমতি পায় না। টেবিলের ওপর খাবার পড়ে থাকলে আর যারই ছোঁবার অধিকার থাক, সুহৃদের নেই। রেফ্রিজারেটরেও হাত দেবার কোনও অধিকার ওর নেই। গীতা যখন ওকে খেতে দেবে, তখনই ও খেতে পাবে। সেই খাওয়া অতি অখাদ্য খাওয়া। পচা পুরোনো বাসি খাবার। নাদুস নুদুস ছেলে শুকিয়ে কাঁটা হয়ে গেছে। ছোটদা থাকলে বাড়ির সবাইকে ডেকে নিয়ে খেতে বসেন টেবিলে। তাঁকে দেখিয়ে সুহৃদের পাতে গীতাকে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও মাংসের টুকরো দিতে হয়। বাইরের লোকের সামনেও গীতা দেখাতে চায় নিজের ছেলেকে সে ভালবাসে, কিন্তু কারও বুঝতে খুব বেশি দেরি হয় না তার সুচতুর চরিত্র। গীতা তার স্বার্থের জন্য নিজের হিংস্র রূপটি যথাসম্ভব ঢেকে রেখে আহ্লাদি গলায় কথা বলে যে কোনও কাউকে গলিয়ে মজিয়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে পারে, এমনই সে পাকা। কিন্তু শেষ অবদি কারও সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব টেকে না দীর্ঘ দিন। স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে গীতা হাওয়া।
তারপরও আমরা যাই নয়াপল্টনে। না গিয়ে পারি না। সুহৃদকে একবার চোখের দেখা দেখতে যাই। মা সুহৃদের জন্য ডজন ডজন মুরগি নিয়ে, নানারকম ফলমূল নিয়ে যান ঢাকায়। মার হাত থেকে জিনিসপত্র নিয়ে গীতা গোপনে রেখে দেয়। সুহৃদকে জানতেও দেয় না মা তার জন্য অনেক খাবার এনেছেন। আমি আগে যেমন মাইনে পেলেই সুহৃদকে নিয়ে যেতাম দোকানে, সুহৃদ যত খেলনাই পছন্দ করত, কিনে দিতাম। এখনও হাতে টাকা এলেই সুহৃদের জন্য জামা কাপড় আর তার পছন্দের খেলনা কিনে ঢাকা নিয়ে যাই, গীতা আমার হাত থেকে সব নিয়ে আলমারিতে রেখে দেয়। সুহৃদকে জানানো হয় না, কিছু দেওয়াও হয় না। সব দেওয়া হয় পরমাকে। পরমাকে পরম আদরে মানুষ করছে গীতা। সুহৃদ অবকাশে যে আদর পেত, সেই আদর গীতা পরমাকে দিচ্ছে। পরমা তার বড় ভাইকে গাল দেবার ঘুসি দেবার লাথি দেবার সব রকম অধিকার রাখে, সুহৃদকে পিঠ পেতে কান পেতে সব বরণ করতে হয়। এক বাড়িতে দুই সহোদর ভাই বোন দু রকম ভাবে মানুষ হচ্ছে। যে সুহৃদ নিজে কখনও গোসল করেনি, মা তাকে কুসুম গরম জলে সাবান মেখে তাকে গোসল করিয়ে ঘরে এনে সারা গায়ে জলপাই তেল মেখে চুল আঁচড়ে দিতেন সিঁথি করে, সেই সুহৃদকে এখন একা গোসল করতে হয়, নিজে সে সাবান মাখতে পারে না, শ্যাম্পু করতে পারে না, গায়ে কোনওরকম জল ঢেলে চলে আসে। ২৫ পরমাকে নিজে হাতে গীতা গোসল করিয়ে আনে। পরমার জন্য ভাল জামা কাপড়, ভাল জুতো, ভাল খেলনা। সুহৃদর জন্য যা কিছু সব পুরোনো, সব মলিন। সুহৃদের জন্য একটি শক্ত তোশকের ছোট বিছানা। পরমার জন্য নরম গদির পালংক। পরমার গালে চুমু, সুহৃদের গালে চড়। পরমার গায়ে বেবী লোশন মেখে চুল আঁচড়ে দিতে দিতে গীতা বলছে, কি গো রাজকন্যা, তোমাকে একটু আঙুর দেই।
না।
প্লিজ একটু খাও।
না।
তুমি আমার মা, মা গো, একটু খাও।
পরমা মাথা নাড়ে, সে খেতে রাজি।
পরমা রাজি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, গীতা হাঁক দিল, এই সুহৃদ, পরমারে আঙুর আইন্যা দে।
সুহৃদ দৌড়ে তার মার আদেশ পালন করে।
সুহৃদ আবদার করে, আমিও একটু আঙুর খাই?
গীতা ধমকে ওঠে, না।
পরমা জুতো পরবে। গীতা হাঁক দেয়, সুহৃদ জুতা নিয়া আয়।
সুহৃদ জুতো নিয়ে এল। কিন্তু একটি ধুম শব্দের কিল উপহার পেল।
জুতা মুইছ্যা নিয়া আয়।
ধুলো মুছে নিয়ে এল সুহৃদ।
যা, পরমার পায়ে পরাইয়া দে জুতা।
সুহৃদ জুতো পরাতে পরাতে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলে, ‘আমি কি ওর চাকর?’ গীতা ছুটে এসে নিজের পায়ের জুতো খুলে সেই জুতো দিয়ে সুহৃদের পিঠে সজোরে আঘাত করতে করতে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, ‘হ তুই ওর চাকর। অন্যদিন তো পরাস জুতা, আইজকা মুখ দিয়া কথা বাইর হয় কেন? আইজকা তর সাহস বাড়ল কেমনে? কারে দেইখা সাহস বাড়ছে? মনে করছস কেউ তরে বাঁচাইতে পারবো আমার হাত থেইকা?’
আমার চোখের সামনে ঘটে এগুলো। আমার আর সয় না। বেরিয়ে যাই ঘর থেকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একা কাঁদি। আমরা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। কোনও মা কি পারে এরকম ব্যবহার করতে নিজের সন্তানের সঙ্গে? সৎ মায়ের নির্মমতার অনেক গল্প শুনেছি। সব গল্পই হার মানে গীতার কাছে। মা বলেন, ‘গু ফালায় নাই মুত ফালায় নাই, হাঁটা শিখায় নাই, কথা শিখায় নাই, ছয় বছর পরে একটা তৈরি ছেলে পাইছে, ছেলের জন্য কোনও টান নাই।’ তাই বা কেন হবে, ভাবি। হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে পঁচিশ বছর পর ফিরে পেলেও তো মায়ের আদর মরে যায় না।
বাবাও যান সুহৃদকে দেখতে। বাবার কাছেও গীতা সুহৃদকে ভিড়তে দিতে চায় না। সুহৃদের প্রাণ ফেটে যায় কাছে বাবার কাছে যাবার জন্য। ধমকে কান মলে পিঠে কিল বসিয়ে সুহৃদকে স্থির করে রাখা হয় যেখানে গীতা চায় সে স্থির হোক। বাবা ফিরে আসেন অবকাশে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে। বলেন, ‘গীতা কি ভুইলা গেছে যে সুহৃদ তার পেটের ছেলে!’
সুহৃদের দুঃসহ অবস্থা দেখে প্রতিবারই আমরা এক বুক দুঃখ আর হতাশা নিয়ে ফিরি। এমনও হয় যে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দরজায়, গীতা দরজা খুলছে না। মা নিজে বাসে চড়ে গরমে ভুগতে ভুগতে ধুলোয় ধোঁয়ায় কালো হতে হতে বাসের গুঁতো ধাককা খেতে খেতে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় গিয়ে ছোটদার বাড়ির বারান্দায় তিন চার ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছেন। গীতা ঘরে ছিল, তবুও দরজা খোলেনি। সুহৃদ একদিন জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে মাকে দেখে গীতাকে ডেকেছে দরজা খোলার জন্য। গীতা ওঠেনি। নিজে সে চেয়ার টেনে এনে দাঁড়িয়ে দরজা খুলেছে নিজে। এটুকু সাহস করার জন্য সুহৃদের ওপর তাণ্ডব চলে কয়েকদিন। আমিও অনেকদিন বারান্দায় অপেক্ষা করে ফিরে এসেছি। যদি দরজা খোলে তবে বসতে বলে না, যদি নিজে বসিও, তবে খেতে ডাকে না, বাইরে থেকে খেয়ে আসি। শোবার জন্য বিছানা দেয় না। বৈঠক ঘরের সোফায় রাত কাটাই। এরকম যাওয়া কেবল সুহৃদের জন্য। অনেকবার ভেবেছি যাবো না, কিন্তু গেলে সুহৃদের যে ভাল লাগে, সুহৃদ যে জেনে সুখ পায় যে আমরা তাকে দেখতে গিয়েছি, সে কারণে যাই। সুহদকে আমার উপস্থিতির সুখ দেওয়ার জন্য গীতাকে নানা উপঢৌকনে ঢেকে যেন তাকে খুব ভালবাসি, তাকে (ছেলেমেয়েসহ) রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাই, থিয়েটারে নিয়ে যাই, উৎসবে মেলায়, দোকান পাটে, যেখানে গেলে তার ভাল লাগবে যাই, যেন তার মত এত হৃদয়বতী জগতে নেই বলেই তাকে এমন খাতির করছি। আসলে যে সবই সুহৃদের জন্য করি সে কথা গীতাকে বলি না। সুহৃদ যেন আমার সান্নিধ্য পায়, আমার সঙ্গ সুহৃদকে তার শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে খানিকটা প্রাণবায়ু দেয় সে কারণে যে করি, বলি না। গীতা বোঝে ঠিকই, আমিও বুঝি সে বোঝে। কিন্তু গীতা যা বোঝে, তা সে মনে মনেই রাখে, সুহৃদকে বুঝতে দিতে চায় না। অনেক দিন এমন হয়েছে যে টাকা ভর্তি ব্যাগটি সোফায় রেখে পেচ্ছ!বখানায় গেলাম, ফিরে এসে দেখি ব্যাগ পড়ে আছে, ভেতরে একটি টাকাও নেই। সোনার কানের দুল খুলে স্নান করতে গেলাম, ফিরে দেখি দুল নেই। গীতা যদি এসব নিয়ে নিজে খুশি থাকে, তবু সে খুশি হোক। তার মন খুশি থাকলে হয়ত সুহৃদকে কী করে কষ্ট দেওয়া যায় তার পরিকল্পনা আঁটা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। আমি হারানো জিনিসের জন্য কেবল মনে মনেই দুঃখ করি, অভিযোগ করি না। খাতির পরমাকেও করতে হয়, পরমাকে কোলে তুলে তার অসুন্দর মুখটিকেও আহা কী সুন্দর বলতে হয়, পরমাকে জিনিসপত্র দিলে গীতা খুশি হয় বলে দিতে হয়। গীতা খুশি হলে বসতে বলবে, গীতা বসতে বললে সুহৃদের সঙ্গে আমার দেখা হবে, দেখা না হলেও চোখাচোখি হবে, হয়ত সুহৃদ ফাঁক পেয়ে আমাকে একটু ছুঁয়ে যেতেও পারবে। এই স্পর্শটুকু সুহৃদের জন্য ভীষণ প্রয়োজন। গীতার মা ভাই বোন প্রায়ই যায় ছোটদার বাড়িতে। তাদেরও দেখেছি পরমাকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে আর সুহৃদকে গালাগাল করতে। গীতাকে খুশি করা গীতার আত্মীয়দের অর্থনৈতিক দায়িত্ব। একবার সুহৃদ পড়ে গিয়ে হাত ভাঙল, গীতা কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় না, আমিই সুহৃদকে নিয়ে যাই। ডাক্তার এক্সরে করে দেখলেন হাড় ভেঙেছে। হাত প্লাস্টার করে ব্যাণ্ডেজ করে গলায় ঝুলিয়ে দিলেন নব্বই ডিগ্রি কোণে, হাড় জোড়া লাগতে এক মাস লাগবে বলে দিলেন। সুহৃদ ডাক্তারখানা থেকে বাড়ি ফিরতেই গীতা টেনে সব প্লাস্টার আর ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলেছে। বলেছে, ‘হাতে কিছু হয় নাই। সব ওর শয়তানি।’
গীতার সব দুর্ব্যবহার সহ্য করি আর মনে মনে বলি আমাদের ওপর করুক তার যা ইচ্ছে তাই, তবু সুহৃদের ওপর যেন কোনও অত্যাচার না করে। সুহৃদ বোঝে সব। সুহৃদও গীতার নির্মমতা নিষ্ঠূরতা সহ্য করে, যেন আমাদের সঙ্গে কোনও দুর্ব্যবহার না করে গীতা। ছ বছর বয়স মাত্র সুহৃদের। সুহৃদ তার সমস্ত আবেগ সমস্ত স্বাভাবিক প্রকাশ সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে রেখে কৌশলী হয়ে ওঠে। সে প্রাণপণে তার মাকে খুশি করতে চায়, যেসব কথা বললে তার মা খুশি হবে, সেসব কথা বলে। নিজের মার কিঞ্চিৎ পরিমাণ সহানুভূতি পাবার জন্য এই টুকুন বাচ্চাকে অভিনয় করতে হয়।
বিমানের চাকরিতে বিদেশ ঘুরে ছোটদা সপ্তাহ দু সপ্তাহ পর ফেরেন। ছোটদা ফিরতেই গীতার নালিশ শুরু হয় সুহৃদের বিরুদ্ধে। সুহৃদ খারাপ, সুহৃদ বাজে, ইশকুল থেকে অভিযোগ করেছে, সুহৃদ কথা শোনে না, পরমাকে মেরেছে ইত্যাদি আরও নানা কিছু বানিয়ে বানিয়ে। গীতার সুখ হয় যখন ছোটদা সুহৃদকে ধমকান। ছোটদার কোলে গীতা পরমাকে বসিয়ে দেন, যেন তিনি আদর করেন পরমাকে। পরমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ গীতা। পরমা পড়ায় ভাল, ছড়ায় ভাল, চড়ায় ভাল, নড়ায় ভাল, মন ভরায় ভাল। পরমার এটা লাগবে, ওটা লাগবে। কেবল পরমাকে নিয়েই গীতার সব গল্প। ছোটদা লক্ষ্য করেন সুহৃদের ওপর অনাচার হচ্ছে। লক্ষ্য করেন ঠিকই, কিন্তু গীতার সমালোচনা করার কোনও সাহস তাঁর নেই। তিনি টাকা পয়সা যা কামান তার সবটাই গীতার হাতে তুলে দেন, গীতার প্রতিটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই তাঁর কাজ। গীতার ত্রাসের রাজত্যে সুহৃদ তো ভয়ে পাথর হয়ে থাকে, ছোটদাও তটস্থ। গীতা তার বিমান আপিসের ছোটখাটো রিসেপশনিস্টের চাকরিটি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। সম্পূর্ণই সে গৃহবধূ। কিন্তু গৃহবধূর জীবন সে যাপন করে না। জাঁকালো একটি জীবন তার, নিজে গাড়ি চালাচ্ছে, যেখানে খুশি সেখানে যাচ্ছে, টেনিস খেলতে যাচ্ছে, সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে যাচ্ছে। কোনও স্বনির্ভর সম্পন্ন মেয়ে যে স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখতে পারে না, গীতা গৃহবধূ হয়েও তা অবাধে ভোগ করে। গীতার নির্ভয়তা, নিঃশঙ্কতা আমাকে বিমুগ্ধ করে, একই সঙ্গে তার অনুদারতা, তার ক্রূরতা, খলতা আমাকে বিচলিত করে।
মা বলেন, ‘সুহৃদের ব্রেইন না আবার খারাপ হইয়া যায়। ছেলেডা স্বাভাবিক ভাবে মানুষ হওয়ার সুযোগ পাইতাছে না।’ মা এও ভাবেন ধীরে ধীরে কাছে থাকতে থাকতেই গীতার হয়ত ওর জন্য ভালবাসা জন্মাবে। আমরাও ভেবেছিলাম, কিন্তু সুহৃদের জন্য তার কোনও ভালবাসা জন্মায় না। সুহৃদের ওপর তার অত্যাচারের কারণ একটিই, সেটি হল ও তাকে ভালবাসে না, ভালবাসে আমাদের। আমাদের কাছ থেকে ওকে দূরে সরিয়েও সে আমাদের জন্য ওর ভালবাসা এতটুকু ম্লান করতে পারেনি, এ কারণেই তার আরও জেদ। তার হিংসে, তার জেদ, তার ক্ষুদ্রতা তার সমস্ত বোধবুদ্ধি লোপ পাইয়ে দেয়।
আমরা, এমনও হয়েছে, মাস চলে গেছে যাইনি সুহৃদকে দেখতে, এর একটিই কারণ যেন গীতা আর সুহৃদের সম্পর্ক যেন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সুহৃদকে যেন আর সব শিশুর মত বেড়ে উঠতে দেয় সে। ঈদের সময় ছোটদা যখন বউ বাচ্চা নিয়ে বেড়াতে আসেন অবকাশে, সুহৃদ ফিরে পায় তার জগত। আগের মত উচ্ছঅল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খেলে, দৌড়োয়, কথা বলে, হাসে, কাঁদে। আমরা কাছে আছি বলে করে ও, ঠিক আগের মত করে। কিন্তু গীতার সামনে দাঁড়ালে আবার ও পাথর। প্রতি ঈদেই একটি ঘটনা ঘটে, ও কিছুতেই ফিরে যেতে চায় না ঢাকায়। যাওয়ার সময় হলেই ও লুকিয়ে থাকে, ভয়ে কাঁপে। ওকে জোর করে টেনে ধরে মেরে গাড়িতে ওঠাতে হয়। প্রতিবার যাওয়ার সময় ওর আর্তনাদে অবকাশ কাঁপে। সারা পাড়া কাঁপে।
গীতা কোনওদিনই পারে না সুহৃদকে ভালবাসতে। সুহৃদ কোনওদিনই পারে না তার মাকে ভালবাসতে।
দীর্ঘ দীর্ঘ দিন সুহৃদহীন অবকাশে কোনও প্রাণ থাকে না। প্রেতপুরীর মত লাগে একসময়ের কলরোলে কলতানে মুখর অবকাশটিকে। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনি অবকাশের।
০৪. তোমাকে পারিনি ছুঁতে, তোমার তোমাকে
রুদ্রকে নিয়ে যে যৌথজীবনের চমৎকার স্বপ্ন দেখেছিলাম, সে স্বপ্ন-পোড়া-ছাই আমার সর্বাঙ্গে ত্বকের মত সেঁটে থাকে। জানি যে রুদ্রর সঙ্গে জীবন যাপন সম্ভব নয়। জানি যে যার যার জীবনের দিকে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। জানি এখন সব ধুলোকালিছাই ধুয়ে মুছে পরিচ্ছত হওয়ার সময়। তবু সময় গড়াতে থাকে, দিন পুড়তে থাকে নির্জন রোদ্দুরে, রাতগুলো অন্ধকারে তক্ষকের মত ডাকতে থাকে আর উঠোনের উচ্ছিষ কাঠের মত বসে থাকি আমি নিজেকে নিয়ে। এই জীবনকে নিয়ে ঠিক কোনদিকে যাব, কোথায় গেলে নেই নেই করা হু হু হাওয়া আমার দিকে বদ্ধ উন্মাদের মত ছুটে আসবে না বুঝে পাই না। জীবনটিকে একবার পালক আরেক বার পাথর বলে বোধ হতে থাকে। এই যে জীবন, যে জীবনটি খুঁড়োতে খুঁড়োতে এসে শেষ অবদি বসেছে আমার গায়ে, কখনও মোটেও টের পাই না, আবার আমার ঘাড় পিঠ সব কুঁজো হয়ে যায় এই জীবনেরই ভারে। এই জীবনটিকে আমি ঠিক চিনি না, জীবনটি আমারই ছিল অথচ আমার ছিল না। দীর্ঘ দীর্ঘ বছর ধরে আমি এর যা কিছু পানীয় সব ঢেলে দিয়েছি একটি আঁজলায়, নিজের তৃষ্ণার কথা আমার একবারও মনে পড়েনি। পরে কাতর হয়ে হাত বাড়াতে গিয়ে দেখছি জলহীন শুষ্ক মরুর মত পড়ে আছে জীবন। আমারই ঘড়ায় আমার জন্য কিছু অবশিষ্ট নেই। প্রতিদিন সেই আগের মত আবার ঠিক আগের মতও নয়, ডাকপিয়নের শব্দে দৌড়ে যাই দরজায়। কারও কোনও চিঠির জন্য আমি অপেক্ষা করে নেই, জানি। কিন্তু চিঠির ভিড়ে চিঠি খুঁজি, একটি চেনা চিঠি খুঁজি, যে চিঠির শব্দ থেকে একরাশ স্বপ্ন উঠে ঘুঙুর পরে নাচে, যে চিঠির শব্দ থেকে রুপোলি জল গড়িয়ে নেমে আমাকে স্নান করায়। জানি যে আগের মত তার কোনও চিঠি আমি আর কোনওদিন পাবো না, তারপরও ভেতরে গুঁড়ি মেরে বসে থাকা ইচ্ছের! অবাধ্য বালিকার মত হুড়মুড় করে কী করে যেন বেরিয়ে আসে। আসলে এ আমি নই, আমার ভেতরের অন্য কেউ একটি চেনা হাতের লেখা খোঁজে চিঠির খামে। আমি নই, অন্য কেউ চেনা হাতের লেখার চিঠি না পেয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে। প্রতিদিন ডাকপিয়নের ফেলে যাওয়া চিঠি হাতে নিয়ে সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনি আমি। আমার নয়, অন্য কারও। কোথাও কোনও গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে থাকা সেই অন্য কাউকে ঠেলে সরাতে চাই দূরে, পারি না। রুদ্রর চিঠি আমি আর কখনও পাবো না জানি, তবু বার বার ভুলে যাই, প্রতিদিন ভুলে যাই যে পাবো না। ছাইএর ওপর উপুড় হয়ে অপ্রকৃতস্থের মত খুঁজতে থাকি তিল পরিমাণ স্বপ্ন কোথাও ভুল করে পড়ে আছে কি না।
ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে বইমেলায় প্রতি বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে চেনা কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, এমনকী কারও কারও সঙ্গে মেলার ভেতর চায়ের দোকানে বসা হয়, আড্ডা হয়, কিন্তু চোখ খুঁজে ফেরে একটি চেনা মুখ, একজোড়া চেনা চোখ। চোখের তৃষ্ণাটি নিয়ে প্রতিরাতে ঘরে ফিরি। তবে একদিন দেখা মেলে তার, আমার ভেতরের আমিটি আমাকে পা পা করে তার দিকে এগিয়ে নেয়। ইচ্ছে করে বলি, ‘তুমি কি ভাল আছো? যদি ভাল আছ, কি করে ভাল আছ? আমি তো ভাল থাকতে পারি না! এই যে আনন্দ করছ, কি করে করছ? আমি তো পারি না, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন পারি না।’ কোনও কথা না বলে তাকে দেখি, বন্ধু বেষ্টিত রুদ্রকে অপলক চোখে দেখি। ইচ্ছে করে বেষ্টন ভেদ করে রুদ্রর সামনে গিয়ে দাঁড়াই, হাত ধরে তাকে নিয়ে আসি, সেই আগের মত দুজন পাশাপাশি হাঁটি মেলার মাঠে। ইচ্ছেগুলো নাড়ি চাড়ি, ইচ্ছেগুলোর সঙ্গে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলি। ইচ্ছের চোখে কালো রুমাল বেঁধে দিয়ে দৌড়ে পালাই, জিতে গেছি ভেবে অট্টহাসি হাসি। আমার হাসিই, নিজের কানে শুনি কান্নার মত শোনাচ্ছে। রুদ্রর নতুন কবিতার বই বেরিয়েছে, তার আনন্দ আমি কেবল দূর থেকে অনুভব করি। দিয়েছিলে সকল আকাশ, তার নতুন বইটি কিনে যখন বাড়িয়ে দিয়েছি তার দিকে অটোগ্রাফ নিতে, রুদ্র কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা চোখে আমাকে দেখে প্রথম পাতায় লেখে, যে কোনও কাউকে। হ্যাঁ, আমি এখন রুদ্রর কাছে যে কোনও কেউ। বইটি হাতে নিয়ে বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকা আমার ওপর ইচ্ছেগুলো বাঁদরের মত লাফাতে থাকে। ছিঁড়তে থাকে আমাকে। রুদ্র কি জানে কী ভীষণ রকম আমি চাইছি যেন সে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করে কেমন আছি আমি, কবে এসেছি ঢাকায়, কতদিন থাকব। চেনা মানুষগুলো সকলেই তো আমাকে জিজ্ঞেস করেছে। রুদ্র কি আমার কম চেনা ছিল! কি করে এমন নিস্পৃহ হতে পারে সে! কেউ কি এত শীঘ্র ভুলে যেতে পারে তার সবচেয়ে আপন মানুষটিকে। প্রশ্নগুলো আমার ইচ্ছেগুলোর কাঁধে সওয়ার হয়ে উৎসবমুখর মেলা ছেড়ে আমার সঙ্গে বাড়ি ফেরে।
মেলার শেষদিকে রুদ্রর সঙ্গে কথা হয়, চা খাওয়া হয় মুখোমুখি বসে। জিজ্ঞেস করি পায়ের কথা। বলে আগের চেয়ে কম দূরত্ব সে ডিঙোতে পারছে এখন। সিগারেট ছেড়েছো? হেসে বলে, ও ছাড়া যাবে না। আর কিছু ছেড়েছে কি না জিজ্ঞেস করি না। আমার শুনতে ভয় হয় যে বাকি নেশাগুলোও তার পক্ষে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। রুদ্র অনেকক্ষণ আমার চোখের দিকে গভীর করে তাকিয়ে থেকে ভারী কণ্ঠে বলে, চল ঝিনেদা চল, কাল ভোরবেলা। আমি যাব কী না, যেতে চাই কী না, কোনও জানতে চাওয়া নয়। তার যেন দাবি আছে আমার ওপর, সেরকম দাবিতেই বলে। যেন রুদ্র জানেই যে আমি যাব। একবার স্পর্শ করলে কেঁদে উঠব অবুঝ বালিকা। কাল ময়মনসিংহে ফেরার কথা আমার, আর হঠাৎ কিনা ঝিনাইদহ যাওয়ার প্রস্তাব। ঝিনাইদহে কবিতার অনুষ্ঠান হচ্ছে, ওখানে আরও কিছু কবি যাচ্ছেন। গতবার, রুদ্রর সঙ্গে আমার যখন বিচ্ছেদ হচ্ছে হচ্ছে, আমরা দুজনই কক্সবাজারে গিয়েছিলাম, সমুদ্রের জলে সিনান করে, তীরের বালুর ওপর সূর্যাস্তের আলোর নিচে বসে কবিতা পড়েছিলাম। কবি মহাদেব সাহা আর নাসির আহমেদ ছিলেন সঙ্গে। লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরা মহাদেব সাহা গামছা কাঁধে নিয়ে, লম্বা পান্তলুন পরে রুদ্র আর নাসির আহমেদ আর হলুদ ক্যাঙ্গারু গেঞ্জি আর জিনস পরে আমি জলে নেমেছিলাম, কাপড়ে জল ঢুকে আমাদের শরীর ভারী করে তুলছিল আর ক্ষণে ক্ষণে আমাদের তার নাড়ির দিকে টেনে নিচ্ছিল ভাটির জল। কী চমৎকার সময় কেটেছিল আমাদের! আমি যাব ঝিনাইদহ, এ যাওয়া কোনও উৎসবের আনন্দে শরিক হওয়ার জন্য নয়। এ কেবলই রুদ্রর পাশে থাকার জন্য। তার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে আমার, আমরা আর স্বামী স্ত্রী নই, কিন্তু এই পৃথিবীতে সবচেয়ে কাছের মানুষ কে আছে আমার রুদ্র ছাড়া! বন্ধু কে আর আছে! দীর্ঘ বছর ধরে এক রুদ্রকেই আমি আপন করে তুলেছি, তাকেই আমি আমার জগত করে তুলেছি। রুদ্র আমাকে দুঃখ দিয়েছে জানি, কিন্তু আমি তো এ কথা অস্বীকার করতে পারি না তাকে যে ভাল বাসি। ঝিনাইদহ যাওয়ার বাস ছাড়ে বাংলা একাডেমি থেকে। পথে আমাদের আলাদা জীবনে যা ঘটছে ছোটখাটো ঘটনা দুর্ঘটনা সব বলি পরস্পরকে। একটি কথাই আমি কেবল লুকিয়ে রাখি, আমার কষ্টের কথা। বলি না রোদহীন শীতার্ত সকালগুলো আমাকে কেমন জমিয়ে বরফ করে রাখে। রুদ্র হঠাৎ বলে, কবিতা শুনবে! প্রিয় কবির কবিতা শুনব না, এ কেমন কথা। রুদ্র, বাসে বসে পাশে বসে, পড়ে, দূরে আছো দূরে।
তোমাকে পারিনি ছুঁতে, তোমার তোমাকে —
উষ্ণ দেহ ছেনে ছেনে কুড়িয়েছি সুখ,
পরস্পর খুঁড়ে খুঁড়ে নিভৃতি খুঁজেছি।
তোমার তোমাকে আমি ছুঁতে পারি নাই।
যেভাবে ঝিনুক খুলে মুক্তো খোঁজে লোকে
আমাকে খুলেই তুমি পেয়েছো অসুখ,
পেয়েছো কিনারাহীন আগুনের নদী।
শরীরের তীব্রতম গভীর উল্লাসে
তোমার চোখের ভাষা বিস্ময়ে পড়েছি —
তোমার তোমাকে আমি ছুঁতে পারি নাই।
জীবনের পরে রাখা বিশ্বাসের হাত
কখন শিথিল হয়ে ঝরে গেছে লতা।
কখন হৃদয় ফেলে হৃদপিণ্ড ছুঁয়ে
বসে আছি উদাসীন আনন্দমেলায়—
তোমাকে পারিনি ছুঁতে — আমার তোমাকে,
ক্ষ্যাপাটে গ্রীবাজ যেন, নীল পটভূমি
তছনছ করে গেছি শান্ত আকাশের।
অঝোর বৃষ্টিতে আমি ভিজিয়েছি হিয়া —
তোমার তোমাকে আজো ছুঁতে পারি নাই।
বাইরের কৃষ্ণচূড়া গাছের লালের দিকে তাকিয়ে থাকি অনেকক্ষণ, উদাসীন আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় লু হাওয়া। রুদ্র তার কবিতার কথা শোনাতে থাকে, ইদানীং সে দুহাতে লিখছে, প্রচুর রাজনৈতিক কবিতা, পাশাপাশি একটি কাব্য নাটকও। রুদ্র তার কবিতার খাতা বের করে নতুন লেখা কবিতাগুলো আমাকে পড়তে দেয়, আমার অনুরোধেই দেয়। লক্ষ্য করি, নিপাত যাক ধ্বংস হোক জাতীয় কবিতা ছাড়া ব্যক্তিগত অনুভবের কবিতাগুলো অন্যরকম, নতুন ধরনের। নতুন ধরনটি ধারণ করতে সময় নেয়, কিন্তু সে যে পুরোনো খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে, তা অনুভব করে প্রশান্তি আসে। নতুন ধরনটি ধীরে ধীরে একটি স্নিগ্ধ মনোরম জগতে নিয়ে দাঁড় করায়, যে জগতে ব্যক্তি রুদ্র অনেক বেশি আন্তরিক,অনেক বেশি গভীর।
ঝিনাইদহে আমরা যে যার কবিতা পড়ি মঞ্চে, অসত্যের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচার অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কবিতা। যার কণ্ঠ যত চিৎকার ওঠে, সে তত বাহবা পায়। যে যত নিকুচি করে সরকারের, সে তত নাম কুড়োয়। এখন এমন হয়েছে যে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কবিতা যারা লেখে, সচেতন মানুষ হিসেবে তাদের গণ্য করা হয় না। রুদ্রকেও দেখেছি সে তার রাজনৈতিক কবিতা নিয়ে যত গর্ববোধ করে, অন্য কবিতা নিয়ে তত নয়। এমন দৈশিক সামাজিক দুঃসময়ে ব্যক্তিক ক্ষুদ্রতা থেকে বেরিয়ে বিশাল আকাশের নিচে মানব বন্ধন রচনা করতে হয়, সম্মিলিত স্বপ্নের গান গাইতে হয়। কবিরা সমাজের বাইরে কোনও আলাদা জীব নয়, অসুস্থ সমাজকে সুস্থ করার দায়িত্ব কবিদেরও। কবিরা এ দেশে খুব জনপ্রিয়, শত শত লোকের ভিড় হয় কবিতার অনুষ্ঠানে, মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব কবিরা নিয়েছেন। রুদ্রও নিয়েছে, স্বৈরাচারি শাসকের বিরুদ্ধে কয়েকটি আগুন আগুন কবিতা পড়ে আসর মাত করে। এমন দৃপ্ত যার কণ্ঠস্বর, এমন যার ক্ষমতা কেবল শব্দগুচ্ছ দিয়ে এক একটি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি বানিয়ে ফেলার, শীতলতা তাকে কী ভীষণ আবৃত করে রাখে। মঞ্চ থেকে নেমে ধীরে হেঁটে, থেমে থেমে হেঁটে রুদ্র পিছিয়ে পড়ে যখন সবাই মিলে আমরা যাচ্ছি কোথাও! অল্প দূর হেঁটেই পায়ের যন্ত্রণা তাকে বারবারই দাঁড় করিয়ে দিলে কাঁধখানা বাড়িয়ে দিই যেন ভর দিয়ে দাঁড়ায়। বড় অসহায় দেখতে লাগে রুদ্রকে। ইচ্ছে করে তার অসুখগুলো এক ফুঁয়ে ভাল করে দিই, ইচ্ছে করে হাত ধরে দৌড়ে যাই দুটো উদ্দাম, উচ্ছঅল, উষ্ণ হৃদয়, সবার আগে, সামনে। ইচ্ছেগুলো দলিত হতে থাকে অগ্রগামীদের জুতোর তলে। ঝিনাইদহের সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্তার বাড়িতে তখন কবি আসাদ চৌধুরী অসংখ্য গুণগ্রাহী নিয়ে বসে গেছেন আলোচনায়। আলোচনা আজকাল একটিই, এরশাদ। এরশাদের পতন কী করে ঘটানো যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন সঠিক হচ্ছে কী না, হাসিনা খালেদা কারও কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে কী হচ্ছে না এসব নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। আলোচনায় অংশ নিতে রুদ্রর আগ্রহ উপচে পড়ে, আমার আগ্রহ হলেও অংশগ্রহণ সম্ভব নয় জানি। আমার মুখে কঠিন কঠিন রাজনীতির শব্দ খুব কম আসে। বিশ্লেষণেও আমি খুব কাঁচা। আর্থ সামাজিক শব্দটির মানে বুঝতেই আমার অনেকদিন লেগেছে। আমি খুব সহজ করে যে জিনিসটি বুঝি তা হল, একটি সুস্থ এবং সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে হলে সবার জন্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, সবার জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্যর ব্যবস্থা করা উচিত। নারী পুরুষের সমান অধিকার, সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা উচিত। অন্ধত্ব, গোঁড়ামি, হিংস্রতা, নৃশংসতা থেকে সমাজকে মুক্ত করা উচিত। এই উচিত কাজগুলোর জন্য দক্ষ এবং সৎ নেতৃত্ব প্রয়োজন। কিন্তু কার পক্ষে সম্ভব নেতৃত্ব দেওয়া! কেউ বলছে হাসিনা, কেউ খালেদা। যে যার বিশ্বাসের পক্ষে নানারকম যুক্তি দাঁড় করছে। তবে একটি আশার কথা এই, হাসিনা খালিদা দুজন হাতে হাত রেখে শুরু করেছেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন। দুজনের মুখ দেখাদেখি নেই, একে অপরকে গাল দিচ্ছেন এরকমই দেখে অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু গালগাল ভুলে তাঁরা এখন দেশের স্বার্থে জোট বেঁধেছেন। অবশ্য এই জোট বাঁধার পেছনে তাঁদের নিজেদের যত কৃতিত্ব তার চেয়ে বেশি কৃতিত্ব বুদ্ধিজীবিদের। গণতন্ত্রের পক্ষের বুদ্ধিজীবিরা দুই নেষনীকে জোট বাঁধার জন্য প্রেরণা পরামর্শ যা কিছু দরকার দিয়েছেন। কেউ ভুগছে, কেউ ভোগ করছে, কারও কিছু নেই, কারও অঢেল এসব দেখতে দেখতে যদিও গা সওয়া হয়ে গেছে, তবু একটি স্বপ্ন এসে ভর করে আমার চোখে, অন্যায় আর বৈষম্যহীন একটি সমাজের স্বপ্ন। আয়ুঅব্দি জীবনের নিশ্চয়তা। কেবল কিছু মানুষের জন্য নয়, সবার জন্য। ঝিনাইদহে রাত গভীরে হতে থাকে আশায় হতাশায়, স্বপ্নে দুঃস্বপ্নে।
রাতে অতিথিদের ঘুমোবার আয়োজন হচ্ছে যখন, আমার আর রুদ্রর জন্য আলাদা দুটি ঘরের ব্যবস্থা করা হল, কারণ অতিথিদের একজন বাড়ির কর্তার কানে কানে আমাদের বিয়ে-বিচ্ছেদের খবরটি পৌঁছে দিয়েছেন। রুদ্র আর আমি দুজনই আলাদা ঘরের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে এক বিছানায় ঘুমোই। অনেক অনেকদিন পর রুদ্র আমাকে স্পর্শ করে গভীর করে। অনেক অনেক দিন পর রুদ্র আমাকে চুমু খায়। অনেক অনেক দিন পর দুজনের শরীর একটি বিন্দুতে এসে মেশে। একবারও আমার মনে হয় না রুদ্র কোনও পরপুরুষ। মনে হয় না যে আমরা এখন পরষ্পরের অনাত্মীয় কেউ, অবন্ধু কোনও। পরদিন ঝিনাইদহে সকাল হয়, লোকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। কী করে পরপুরুষের সঙ্গে এক ঘরে ঘুমোতে রুদ্রর না হোক, আমার দ্বিধা হল না! আমার হয়নি। যে পাপবোধের কথা অন্যরা ভাবে, সেই পাপবোধের লেশমাত্র আমার মধ্যে নেই। কারও ভ্রুকুঞ্চণ আমাকে স্পর্শ করে না। আমি রুদ্রকে কাগজে পত্রে ত্যাগ করেছি তা ঠিক, তবে কোনও পুরুষকে যদি আমার সবচেয়ে কাছের বলে মনে হয়, সবচেয়ে আপন বলে মনে হয়, সে রুদ্র। এর মধ্যে এক বিন্দু কৃত্রিমতা নেই, এক ফোঁটা মিথ্যে নেই। ভালবাসি এক রুদ্রকেই, যতই তার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ থাকুক না কেন। এই ভালবাসার বোধটি আমি খুব গোপনে গোপনে লালন করি। এই বোধটি আমার একটি হাত নিয়ে রাখে রুদ্রর উষ্ণ কৃষ্ণ হাতে। এই বোধটি একা নিভৃতে বসে থাকে, সংসার যাপনের পরিকল্পনা করে না, ভবিষ্যতের কথা সামান্যও ভাবে না, বোধটি বোধহীন বটে। ঢাকার পথে দুজন যখন কবিতার গল্পে ডুবে যাই, কবিতার দুটি একটি বাক্য পরস্পরকে শোনাচ্ছি, রুদ্র অনেকদিন আগের লেখা একটি কবিতা মুখস্ত বলতে থাকে। তার মনে হয় তার সময়গুলো আসলেই পচে গলে যাচ্ছে।
‘খুলে নাও এইসব পোশাক আমার কৃত্রিমতা
মাংসের ওপরে এই ত্বক, এই সৌন্দর্য মোড়ক
খুলে নাও দিনের শরীর থেকে রোদের ভূমিকা।
গলা পিচের মতোন গলে যাচ্ছে মুহূর্ত, সময়,
গলে যাচ্ছে নারী আর শিশুদের অনাবিল বোধ,
মানুষের মৌলিক বিশ্বাস, গলে যাচ্ছে ভালবাসা
আমি ফেরাতে পারি না সভ্যতার অবিরল ক্ষতি,
আত্মরমনের ক্লেদ, জলে ভাসা পুস্পের সংসার,
শিশুর মড়ক, আমি ফেরাতে পারি না মহামারি,
ভ্রুণ হত্যা, অন্ধকারে জ্বলজ্বলে হননের হাত..
ক্ষমাহীন অক্ষমতা জমে জমে পাহাড় হয়েছে,
পাহাড়ের পাদদেশে সোনারঙ আলস্যের ধান,
আর কিছু দলছুট পরাজিত বিবর্ণ মারিচ।
টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো আমার চেতন,
বিশ্বাসের স্থবির শরীর চাবুকে রক্তাক্ত কর,
ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে ছুঁড়ে দাও আমার আত্মাকে।
মানুষের মৌলিক মুখোশ আমি খুলতে পারি না,
শুধু পুড়ে যেতে পারি, পুড়ে যাই, পোড়াই সৌরভ,
রাতের আগুন এনে নিবেদিত সকাল পোড়াই।’
পা পা করে একটি কষ্ট উঠে আসছে আমাদের দিকে, স্পষ্ট দেখি। ঝাঁক বেঁধে বিষণ্নতাও আসে। কষ্টকে দূর ছাই হাতে সরিয়ে রুদ্র শিমুল নামের একটি মেয়ের কথা বলে, মেয়েটিকে সে গত বছরই প্রথম দেখে মেলায়, মেয়েটিকে নিয়ে অনেকগুলো কবিতা লিখেছে।
‘কি রকম কবিতা?’
‘আমারও ইচ্ছে করে বৈশাখের ঝড়ের সন্ধ্যায়
অন্য কোনো তরুণীর হাত ধরে সুদূরে হারাই,
বৃষ্টি ও বাতাসে মেলি যুগল ডানার স্বপ্ন।
আমারও ইচ্ছে করে ফুটে থাকি অসংখ্য শিমুল।’
‘তারপর?’
‘দুপুরের রোদে পোড়া চিবুকের উদাসীন তিল
ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে ভালবাসা, নীল চোখ, চাঁদের শরীর
আমারও ইচ্ছে করে আঙুলে জড়াই মিহি স্মৃতি,
স্বপ্নের কপাল থেকে ঝরে পড়া চুলগুলো আলতো সরাই।’
‘আর কী কী ইচ্ছে করে?’
‘ইচ্ছে করে নগরের নিয়ন্ত্রিত পথে
সমস্ত নিষেধ মানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
সড়কের মাঝখান বেয়ে হেঁটে যাই
আমারও ইচ্ছে হয় কাঁদি।’
‘এ তো সুখের কথা। এতে কাঁদার কি হল? কাঁদবে কেন?’
রুদ্র হেসে বলে, ‘আরে শোনোই না।’
আমিও হাসি বলতে বলতে, ‘আরে বলই না।’
‘আমারও ইচ্ছে করে খুলে দিই হাতকড়া বাঁধা হাত,
চক্রান্তের খল বুকে কামড় বসাই।
আমারও ইচ্ছে করে
টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলি তোমার শরীর।’
‘ছি ছি, এমন কসাইএর মত কথা বলছো কেন? কার শরীর টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে হয় তোমার?’ আমার বঙ্কিম চাহনী বঙ্কিম ওষ্ঠে এসে সরস হতে না হতেই রুদ্র বলে,
‘দৃশ্যকাব্যগুলো পড়েছো? শিমুলকে নিয়ে লেখা।
আমি তোমার নাম জানি না,
দেখলে চিনি।
এখন আমি কোথায় গিয়ে খুঁজবো তোমায়?
খুঁজতে খুঁজতে কোথায় যাবো?
সিরামিকের গাছগাছালি,
ইটের ঝাউ বনের ভেতর
কোথায় আমি খুঁজবো তোমায়?
কোথায় তোমার সৌম সকাল, শান্ত দুপুর?
কোথায় তোমার মুখর বিকেল, একাকি রাত?
খুঁজবো কোথায়–ঝরা পাতায় সাজানো ঘাস
সন্ধ্যাবেলায়? কোথায় খুঁজবো?’
আমি বলি, ‘অনেক খুঁজেছো, দৃশ্যকাব্য দুইএ তোমার ঘুমও যে মেয়েটিকে খুঁজতে গেছে, সকালে টের পেয়েছো। দৃশ্যকাব্য তিনেও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!। নদী পেরোচ্ছে!, সাগর পেরোচ্ছে!, বিস্তৃত মাঠ পেরোচ্ছে!, পাহাড় পর্বত বন বাদাড় সব খুঁজছো, এমনকি আকাশেও খুঁজছো, এত খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত পেয়েছো তাকে?’
রুদ্রর মুখে অমলিন হাসি। বলে সে পেয়েছে তাকে খুঁজে। শিমুলকে। শিমুল নাকি একটুখানি চেয়েছিল প্রথম প্রথম। অত বেশি নিজেকে খুলতে চায় নি। শিমুলের দুপুরগুলো রুদ্র তখন উড়িয়ে দিতে বলছে।
‘মেলার মধ্যে একটুখানি খোলামেলা
একটুখানি কেন?
খোলামেলা একটুখানি কেন?
খুলতে পারো হৃদয় তোমার সমস্তটুক,
দেবদারু চুল খুলতে পারো
ভুরুর পাশে কাটা দাগের সবুজ স্মৃতি
স্বপ্ন এবং আগামীকাল এবং তোমার
সবচে গোপন লজ্জাটিও খুলতে পারো।
উড়িয়ে দিতে পারো তোমার স্মৃতির ফসিল—
উড়িয়ে দাও দুপুর তোমার শিমুল তুলো,
মেঘের খোঁপায় মুখর বিকেল উড়িয়ে দাও,
উড়িয়ে দাও ব্রীজের নিচের য়চ্ছ জলে
স্বপ্নলেখা সবুজ কাগজ।
এ বৈশাখে হাত মেলে চাও ঝড়ের ঝাপটা,
ভেজা মাটির গন্ধে ফেলে পায়ের আঙুল
এ বৈশাখে হাত মেলে চাও জীবন বদল।’
হঠাৎ কী হয় জানি না, চোখ ভিজে ওঠে কী! জানালায় তাকিয়ে আড়াল করি ভেজা চোখ। খোলা জানালা গলে হাওয়ার সঙ্গে ধুলো আসছে উড়ে, যেন সেই ধুলো চোখে পড়েছে বলে দ্রুত মুছে নিচ্ছি, এমন করে মুছি জল। রুদ্রকে বুঝতে দিই না আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে। আমার তো কোনও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কেন হবে! রুদ্রর আর আমার জীবন এখন আলাদা। এখন সে কারও প্রেমে পড়তেই পারে, কাউকে সে বিয়ে করতেই পারে।
হেসে, যেন রুদ্রর এই প্রেম আমাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছে, সুখে আমি ফেটে পড়ছি, এমন স্বরে এবং ভঙ্গিতে বলি, জীবন বদল করতে রাজি মেয়েটি?
রুদ্র বলে যে হ্যাঁ শিমুল বিয়েতে রাজি, তবে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলছে।
দুজন খুব ঘুরে বেড়াচ্ছো?
তা বেড়াচ্ছি।
শিমুল কেমন দেখতে?
অল্প বয়স। সুন্দরী।
বাহ।
বাহ কি?
বেশ ভালো।
রুদ্রর চোখে অপরূপ দীপ্তি। তির তির করে স্বপ্ন কাঁপছে দুটি চোখে।
চুমু খেয়েছো?
খেয়েছি।
শুয়েছো?
চেয়েছিল। আমিই না বলেছি।
তুমি না বলেছো! বল কি? কারণ কি?
বলেছি, বিয়ের আগে শোবো না!
মেয়েটি সত্যি সত্যি শুতে চেয়েছে?
হ্যাঁ, সত্যি।
অবাক হই শুনে। বাঙালি মেয়ে বিয়ের আগে আগ বাড়িয়ে যৌন সম্পর্ক করতে চায় প্রেমিকের সঙ্গে, এমন শুনিনি।
তারপর?
তারপর কি?
শিমুলকে সত্যিই ভালবাসো?
রুদ্র তাকায় আমার চোখে। চোখে ফুটে আছে অসংখ্য শিমুল। চোখ সরিয়ে নিয়ে জানালায়, বাইরের ফুটে থাকা কৃষ্ণচূড়া দেখতে দেখতে, কী জানি কোথাও সে শিমুল খুঁজছে কি না, সুখ-সুখ গলায় বলে, বাসি।
ঠিক?
ঠিক।
কেন জিজ্ঞেস করলে? রুদ্র জিজ্ঞেস করে।
আমি জানালার ওপারে ফসল উঠে যাওয়া নিঃস্ব ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বলি, না এমনি। রুদ্রকে হঠাৎ করে খুব দূরের মানুষ বলে মনে হয়। বন্ধু সে আমার, কিন্তু যেন কাছের কোনও বন্ধু নয়। আপন সে আমার, কিন্ত তত যেন আপন নয়।
গভীর রাতে ঢাকা পৌঁছোলে রুদ্র তার বাড়িতে নিয়ে যায় বাকি রাতটুকু কাটাতে। ইন্দিরা রোডেই রুদ্র একটি নতুন বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। দোতলায় রুদ্রর পেছন পেছন উঠে সোজা তার ঘরে ঢুকি। অচেনা ঘর, অচেনা ঘরটি অচেনারকম করে সাজানো। তবে আমাদের সেই আগের বিছানাটিই আছে, বিছানায় আগের চাদর, আগের নীল মশারি। সব চেনা। কিন্তু কোথায় যেন খুব অচেনা কিছু। বাকি রাতটুকু ঘুমন্ত রুদ্রর পাশে নির্ঘুম কাটাই। রুদ্রর সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক অনেকের ছিল, ওদের সঙ্গে মনের সম্পর্ক কখনও হয়নি, সবসময় সে বলেছে ওদের কাউকে সে ভালবাসে না। এখন কী নিদ্বির্ধায় রুদ্র বলে, কাউকে সে ভালবাসে, কী অবলীলায় তার ভালবাসার গল্প আমাকে শোনায় সে! আলোঅন্ধকারে ঢেকে থাকা ঘরটিকে আবার দেখি, এ ঘরে নিশ্চয়ই শিমুল এসে বসে, শিমুলের চোখের দিকে রুদ্র তার ভালবাসায় কাঁপা চোখদুটো রাখে।
সকাল হলে শুয়ে থাকা রুদ্রর পাশে বসে কপালে দুটো চুমু খেয়ে, ঘন চুলগুলোয় আঙুলের আদর বুলিয়ে বলি, ভাল থেকো। রুদ্র মাথা নাড়ে, সে ভাল থাকবে। বলে, তুমিও ভাল থেকো। রুদ্রকে বিছানায় রেখেই আমি যাই বলে বেরিয়ে যাই। আমার তো যাওয়ারই কথা ছিল।
রাস্তায় বেরিয়ে একটি রিক্সার জন্য হাঁটতে থাকি। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া আমাকে স্পর্শ করছে, অথচ মনে হচ্ছে বৈশাখি কালো ঝড় আমার ভেতরের সবকিছু ওলোট পালোট করে দিচ্ছে, সব বুঝি ভেঙে দিচ্ছে আমার যা ছিল, নিঃস্ব করে দিচ্ছে আমাকে। বড় একা লাগে, কী জানি কেন, বড় একা লাগে। মনে হয় রাস্তায় একটি প্রাণী নেই, আমি একা হেঁটে যাচ্ছি কোথাও, কোথায় যাচ্ছি তা জানি না, কেবল হাঁটছি, পেছনে দৌড়োচ্ছে স্মুতি, ঝাঁক ঝাঁক স্মৃতি। ময়মনসিংহের সেই দিনগুলো দৌড়োচ্ছে, কলেজ ক্যাম্পাস, ক্যান্টিন, প্রেস ক্লাব, বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেইসব দিন, সেই তীব্র তুমুল ভালবাসার দিনগুলো। ভালবাসার সুতোয় গাঁথা সেই স্বপ্নগুলো। স্মৃতিরা আমাকে এমন করে পেছন থেকে জাপটে ধরে, নিজেকে ছাড়াতে এত চেষ্টা করি, পারি না। অক্টোপাসের মত স্মৃতির হাতগুলো আমার কণ্ঠ চেপে ধরে, নিঃশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হতে থাকে।
০৫. পারলৌকিক মুলো
রাস্ট্রপতি এরশাদ জনগণের এরশাদ হঠাও আন্দোলনের চাপে পারলৌকিক মুলো ঝুলিয়েছেন সামনে। সংবিধানে নতুন একটি জিনিস তিনি বলা নেই কওয়া নেই ঢুকিয়ে দিলেন, জিনিসটির নাম রাষ্ট্রধর্ম। এখন থেকে এ দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। কেউ কি দাবি করেছে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা চাই? না কেউ করেনি। দেশে কি মুসলমানদের ধর্ম পালনে কিছু অসুবিধে হচ্ছিল যে রাষ্ট্রধর্ম না হলে তাদের আর চলছিল না? তাও নয়, খুব চলছিল, বেশ চলছিল। বহাল তবিয়তেই ছিল মুসলমানরা। মসজিদ মাদ্রাসা গড়ে গড়ে দেশের বারোটাই বাজাচ্ছিল, যেখানে সেখানে যখন তখন গজাচ্ছিল লোক ঠকানোর পীর, এখন এরশাদ নিজেই ধর্মের ঢোল নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন। নাচুনে বুড়োদের তাল দিচ্ছেন বেশ। রাষ্ট্রের কি কোনও ধর্মের প্রয়োজন হয়! মানুষের না হয় হয়, কিন্তু রাষ্ট্র কি কোনও মানুষ! রাষ্ট্র তো সব ধর্মের সব সংস্কৃতির সব ভাষার মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। রাষ্ট্র যদি নিরপেক্ষ না হয়, রাষ্ট্র যদি অনেকগুলো সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের পক্ষ নেয়, তবে সেই রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে বিরোধ আর বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। হতে বাধ্য। অমুসলমানরা এ দেশে নিরাপত্তার অভাবে ভুগবে, ভুগতে বাধ্য। সভ্যতার দিকে যেতে হলে যে প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করতে হয়, তা রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করা। সভ্য দেশগুলোয় তাই হয়েছে। যে যুগে ধর্ম ছিল রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র, সে যুগকে বলা হয় অন্ধকার যৃগ। অন্ধকার যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত। অন্ধকার যুগে মানুষের বাক স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। আমার আশঙ্কা হয় এই দেশটি ধীরে ধীরে অন্ধকারের অতল গহবরে তলিয়ে যাচ্ছে। আমার আশঙ্কা হয় ধর্ম নামের কালব্যাধির যে জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এতে ভীষণ রকম আক্রান্ত হতে যাচ্ছে দেশের মানুষ। এরশাদ নিজের গদি বাঁচাতে নানারকম ছলচাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছেন, সংসদ বাতিল করে নির্বাচন করলেন, কোনও বড় দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি যেহেতু, ছোট কিছু দল আর সতন্ত্র কিছু লোক নিয়েই লোক ভুলোনো নির্বাচনের খেলা সারলেন। খেলায় জিতে দেখাতে চাইলেন তাঁর রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা কিছুমাত্র অবৈধ নয়। কিন্তু তাঁর এই টোপ কেউ গিলছে না। ক্ষমতার লোভ এমনই লোভ যে আন্দোলনের ভূমিকম্প যখন তার গদি নাড়িয়ে দিচ্ছে, খুঁটি আঁকড়ে ধরার মত করে তিনি রাষ্ট্রধর্ম আঁকড়ে ধরলেন। জনগণের নাকের ওপর পারলৌকিক মুলো ঝুলিয়ে দিলেন। এবার যাবে কোথায় ধর্মভীরুর দল! বিরোধী দলগুলো জোট বেঁধেছে, নানারকম সাংস্কৃতিক দলও জোট বেঁধেছে শহরে গ্রামে সবখানে। এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক জোট থেকে রাষ্ট্রধর্ম বিষয়ে খুব যে কথা বলা হচ্ছে, তা নয়। কারণ ইসলাম যদি কোথাও এসে বসে, সে বসা অবৈধ হোক, একে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার বুকের পাটা সবার থাকে না। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দলগুলো থেকে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর। হাতে গোণা কিছু সাহিত্যিক সাংবাদিক রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করছেন, এটুকুই। এর বেশি উচ্চবাচ্য নেই।
একাত্তরে বাঙালি মুসলমান অত্যাচারি অবাঙালি মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রমাণ করেছে মুসলমান হলেই এক সঙ্গে বাস করা যায় না। একাত্তরে বাঙালিরা প্রমাণ করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতভাগ ছিল সম্পূর্ণ ভুল একটি সিদ্ধান্ত। একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া বাঙালির স্বপ্ন ছিল অবাঙালি মুসলমানদের বিদেয় করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভালবেসে বাংলা নামের একটি দেশ গড়ে তোলা। দীর্ঘ ন মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন একটি দেশ জুটল। শেখ মুজিবুর রহমান দেশ চালাতে শুরু করলেন। একশ একটা ভুল তাঁর থাকতে পারে, নেতা হিসেবে তিনি অসম্ভব জনপ্রিয় হলেও রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁর হাত কাঁচা হতে পারে, কিন্তু বলিষ্ঠ একটি সংবিধান তৈরি করেছিলেন, যে সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর সমাজতন্ত্র সহ ধর্মনিরপেক্ষতা স্থান পেয়েছিল। কোথায় সেই ধর্মনিরপেক্ষতা এখন! কোত্থেকে কোন এক মেজর জিয়া এসে ক্ষমতা দখল করে কোনও কারণ নেই কিছু নেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করে দিলেন। জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও এক সেনানায়ক একটি চরম অন্যায় করলেন সংশোধনের নামে সংবিধানে একটি কালসাপ ঢুকিয়ে দিয়ে। হা কপাল! দেশের কপালে এই ছিল! বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি! এই গান গাওয়ার মত আর বুঝি কোনও মঞ্চ রইল না। জুন মাসের সাত তারিখ, ১৯৮৮ সাল, বাংলার ইতিহাসে একটি কালি মাখা দিন। চমৎকার একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ার সম্ভাবনাকে গলা টিপে হত্যা করার দিন। অনেকটা সামনে এসে বিস্তর অর্জন করে পেছনে শূন্যতার দিকে ফেরার দিন, অসত্য অন্যায় অবিচার আর অন্ধকারের দিকে ফেরার দিন। এক দুই বছর পেছনে নয়, হাজার বছর পিছিয়ে যাবার দিন।
এ সময় শেখ হাসিনাই হতে পারেন সহায়। শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসেছেন একাশি সালে, আওয়ামী লীগের সভানেষনী হয়েছেন। ফিরে আসার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের মানুষ, যারা জিয়াউর রহমানের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন তিনি স্বাধীনতার শত্রুদের এমনকী গোলাম আযমের মত একাত্তরের গণহত্যাকারীকে দেশে ঢোকার অনুমতি এবং অবৈধ ধর্মীয় রাজনীতিকে বৈধতা দিয়েছিলেন বলে, সংবিধানে বিসমিল্লাহ যোগ করা, ধর্ম নিরপেক্ষতা তুলে দেওয়া এসব দুস্কর্ম তো আছেই— শেখ হাসিনার ওপর ভরসা করলেন। কিন্তু এই হাসিনাই এরশাদের ফাঁদে পা দিয়ে জামাতে ইসলামিকে নিয়ে নির্বাচনে যোগ দিলেন ছিয়াশি সালে। খালেদা জিয়া কিন্তু এরশাদের টোপ মোটেও গেলেননি। এরশাদ নিজের ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য নির্বাচনের আয়োজন করেছিলেন, তা বুঝে হাসিনা শেষ পর্যন্ত সংসদ বর্জন করলেন কিন্তু জামাতে ইসলামির মত দলের সঙ্গে ভিড়ে যে কালিটি তিনি লাগিয়েছেন গায়ে, তা খুব সহজে দূর হবে না। তারপরও প্রগতিশীল মানুষের আশা তিনি ক্ষমতায় এলে তাঁর বাবার আদর্শে সংবিধানের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ আবার পুনরুদ্ধার করতে পারেন। কিন্তু আপাতত এরশাদ বিরোধী জোটকে সমর্থন করা যাক, জোটের আন্দোলন যেন দুশ্চরিত্র স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামাতে পারে। সাত বছর আগে ক্ষমতা দখল করেছে ব্যাটা, আজও ছাড়ার নাম নেই। দেশের লোক চাইছে না তাকে, তাতে কি আসে যায়, আমার কাছে অস্ত্র আছে, ধর্ম আছে, আমি এগুলোর ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে গদিতে বসে আয়েশ করব।
কোনও রাজনৈতিক দলের আমি কোনও সদস্য নই, তবু এ মুহূর্তে দুর্যোগের দিন পার হয়ে একটি সুন্দর আগামীর দিকে যাবে বলে যারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তাঁদের ওপর বিশ্বাস রেখে একটি সম্ভাবনার অংকুরের গোড়ায় আমি জল সার দিই।
ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষদ, সকাল কবিতা পরিষদ এবং আরও সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক দল মিলে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট গঠন করা হয়েছে। কবি, সাহিত্যিক, গানের নাচের নাটকের শিল্পী সব জড়ো হল এই জোটে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দীপ্ত এক একজন মানুষ, সমাজ সচেতন মানুষ, সকলে দেশের মঙ্গল কামনা করে, সকলেই চায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সত্যিকার গণতন্ত্র, সুস্থ সামাজিক পরিবেশ। আমীর হোসেন রতনকে জোটের প্রধান করা হল। আশ্চর্যরকম পরিশ্রমী আর শক্তিমান মানুষ এই রতন। নিজের উদ্যোগে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে তিনি মুকুল নিকেতন নামে একটি ইশকুল খুলেছেন মহারাজা রোডে। সেই ইশকুল ছোট্ট একটি বাঁশের ঘর থেকে ধাঁ ধাঁ করে দালান হয়ে গেল। বছর বছর ছাত্র ছাত্রী বাড়ছে। গাধা পিটিয়ে মানুষ করার মত তিনি ছাত্র ছাত্রী মানুষ করেন মুকুল নিকেতনে। তিনি একটি শব্দ খুব পছন্দ করেন, ডিসিপ্লিন। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের এই ডিসিপ্লিনের শিক্ষা দেন। যে কোনও জাতীয় দিবসে সার্কিট হাউজের মাঠে যখন কুচকাওয়াজ হয়, মুকুল ফৌজএর প্যারেড দেখতে হয় অপলক মুগ্ধতা নিয়ে। ময়মনসিংহের গ্রাম যখন বন্যায় ভাসছে, মানুষের বাড়িঘর ডুবে গেছে, গরুছাগল মরে গেছে, ভাত নেই কাপড় নেই, সেসময় রতন তাঁর বাহিনী নিয়ে জল পেরিয়ে পৌঁছে গেলেন দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সাহায্য পৌঁছে দিতে। পাহাড় সমান কাজ রতনের, তাঁর ঘুমোবার গোসল করবার খাবার সময় নেই। সকলের আগ্রহে অনুরোধে রতন জোটের কাজ হাতে নিলেন। তাঁর হাজার কাজের মধ্যে আরেকটি কাজ যোগ হল। কাজ পেলেই খুশি থাকেন রতন, সকলের প্রিয় রতনদা। বুড়ো বয়সে আত্মীয় স্বজনের চাপে তিনি বিয়ে একটি করেছিলেন, কিন্তু সুন্দরী বালিকা বধূটিও তাঁকে ঘরে বাঁধতে পারেনি। রতন পড়ে থাকেন বাহির নিয়ে। রতনের মত অমন বেপরোয়া না হলেও, আমারও অনেকটা বাহির নিয়ে কাটে। সকাল কবিতা পরিষদে কবির ভিড় তো আছেই, যেহেতু বেশির ভাগ কবিই আবৃত্তিতে কাঁচা, কবি নয় কিন্তু কবিতা যারা ভাল পড়ে, তাদেরও সদস্য করে নিই। মূল কাজটি এখন আগুন আগুন কবিতা নিয়ে পাণ্ডুলিপি তৈরি করা, বৃন্দ আবৃত্তির কায়দা কানুন শিখিয়ে দেওয়া। পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হয় রাত জেগে , একশ কবিতার বই ঘেঁটে। নতুন ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রায় বিকেলে অবকাশের সামনের ঘরে মহড়া চলে। কবির চেয়ে বেশি আমি আবৃত্তিশিল্পী হয়ে উঠি। ঘরে দিন রাত্তির কাজী সব্যসাচী থেকে শুরু করে হালের জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি চলছে। কবিতা লেখাই শুধু শিল্প নয়, কবিতা পড়াও একটি শিল্প। এই শিল্পের তরে সময়পাত করে বেশ ভাল কাজই হয়, জোটের অনুষ্ঠানে কখনও একক কণ্ঠে কখনও সমস্বরে পড়া সকাল কবিতা পরিষদের কবিতা শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে। অল্প দিনেই সংগঠনটি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে শহরে। সকালের ডাক পড়তে টাউন হলে, পাবলিক হলে, বড় ছোট যে কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। জোটের মধ্যে সকাল কবিতা পরিষদ অন্যতম একটি দল, সকাল না হলে এ অনুষ্ঠান জমবে না, ও অনুষ্ঠান ভেস্তে যাবে, শেষে এমন। রাজনৈতিক এই দুঃসময়ে রুখে ওঠার প্রেরণা চাই, উত্তেজনা চাই, গায়ের লোম দাঁড়িয়ে করিয়ে দেওয়ার মত কবিতা চাই – এমন সব কবিতাই আছে সকাল কবিতা পরিষদের আবৃত্তিশিল্পীদের কণ্ঠে। বেশির ভাগ কবিতাই রুদ্রর, নির্মলেন্দু গুণ, শামসুর রাহমান, মহাদেব সাহাও আছেন, পশ্চিমবঙ্গের কবিদের কবিতায় জ্বালাও পোড়াও সাধারণত থাকে না, তাই তাদের কবিতা থেকে খুব কমই বাছাইএ টিকেছে। দলের নাম হলে আবৃত্তিশিল্পীর ভিড় বাড়তে থাকে। ভিড়ের মধ্য থেকে যাচাই করে বাছাই করি। প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে সকাল কবিতা পরিষদ থেকে সমাজ পরিবর্তনের কবিতা এই বক্তব্য দিয়ে চমৎকার একটি অনুষ্ঠান করে ফেলি, পুরো অনুষ্ঠানটি আমি পরিচালনা করি নেপথ্যে থেকে। সৈয়দ শামসুল হককে বলেছিলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হওয়ার, তিনি এককথায় রাজি হয়ে ঢাকা থেকে চলে এলেন। সৈয়দ হক কথা বলায় বেশ পারদর্শী, তিনি মুগ্ধ করলেন অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের। প্রতিবাদের কবিতা, শান্তির জন্য কবিতা এসব কোনও রকম বারোই দিবস তেরোই দিবস ছাড়াই হচ্ছে, পঁচিশে মার্চ, ষোলই ডিসেম্বরে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট থেকে মৌন মিছিলে নেমে পড়ছি। একুশে ফেব্রয়ারিতে অনেকবছর ময়মনসিংহে থাকা হয়নি, একুশের ভোরবেলায় চিরকালই আমার ঘুম ভাঙত আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি গাইতে পারি র সুর শুনে। রাস্তায় সাদা পোশাক পরে খালি পায়ে ফুল হাতে গান গাইতে গাইতে শহীদ মিনারের দিকে ফুল দিতে যাচ্ছে মানুষ, এর চেয়ে সুন্দর এর চেয়ে পবিত্র দৃশ্য আমার মনে হয় না জগতে আর কিছু আছে। এই পথশোভা আমাকে কেবল ঘুম থেকে জাগাতো না, চেতনার দুয়োর হাট করে খুলে স্পন্দিত করত জীবন। রফিক সালাম বরকতের জন্য আমার খুব গৌরব হয়, বাঙালি বলে নিজের জন্যও গৌরব হয়। ভোরের হাওয়া আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো সুরটি তার পাখায় করে নিয়ে এসে আমাকে এমন গভীর করে স্পর্শ করে যে আমাকে কাঁদতে হত। এখনও কাঁদতে হয়। ষোলই ডিসেম্বরে জোটের মিছিলে যখন আমরা ময়মনসিংহের পথে ফুলের স্তবক হাতে হাঁটছি বিজয় স্তম্ভের দিকে, মিছিলে যারা গান জানে গাইছে বিজয়ের গান, স্বাধীনতার গান, গানের কণ্ঠ থেমে এলে যতীন সরকার বললেন জয় বাংলা বাংলার জয় গাও, ওরা গাইতে শুরু করলে মিছিলের এক প্রান্ত থেকে গুনগুন আপত্তি ওঠে, আপত্তির দিকে তাকান যতীন সরকার, আমিও। আপত্তির প্রতিবাদ জানালে জয় বাংলা বা একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি এসব গান আওয়ামী লীগের গান বলে অভিযোগ করে কেউ কেউ। এই মিছিলে দলমত নির্বিশেষে সকলে বিজয় দিবসের আনন্দ করছি, সুতরাং কোনও নির্দিষ্ট দলের গান গাওয়া চলবে না। যতীন সরকার চেঁচিয়ে ওঠেন, এগুলো আওয়ামী লীগের গান হবে কেন? এগুলো মুক্তিযুদ্ধের গান। আমি মাথা নোয়াই লজ্জায়। একাত্তরে যুদ্ধের সময় যে গানগুলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বাজত, যে গান শুনে মুক্তিযোদ্ধারা প্রেরণা পেয়েছে, যে গান শুনে দেশ স্বাধীন করার উৎসাহ নিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছে, দেশকে বাঁচাতে গিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে প্রাণ দিতে দ্বিধা করেনি, সে গানগুলোকে আজ আমাদের সবার গান বলে অস্বীকার করার যে লজ্জা, সেই লজ্জায় আমি মাথা নোয়াই। মিছিলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থক আছেন অনুমান করি। গানের দলীয়করণ নতুন নয়। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় থাকাকালীন শাহনাজ রহমতুল্লাহর প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ গানটি রেডিও টেলিভিশনে খবরের আগে পরে আকছার বাজানো হত। সুতরাং গানটি জাতীয়তাবাদী দলের গান হিসেবে নাম লেখালো। এরশাদও জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে একটি দেশাতব্ববোধক গান বেছে নিলেন নিজের দলের জন্য। হা কপাল! গানেরও মুক্তি নেই, গানকেও কোনও না কোনও দলে নাম লেখাতে হয়। বিজয় স্তম্ভে জোটের পক্ষ থেকে যতীন সরকার আর আমাকে এগিয়ে দেওয়া হয় ফুলের স্তবক অর্পণ করতে। যতীন সরকারের মত এত বড় একজন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই কাজটি করতে পেরে ধন্য হই। তাঁর মত জ্ঞানী লোকের সংস্পর্শে আসার যোগ্যতা আমি খুব ভাল করে জানি যে আমার নেই।
আমি খুব কম লোকেরই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে পছন্দ করি, যতীন সরকার সেই কম লোকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান একজন। যে কোনও বিষয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন। সে সব কথা কেবল বলার জন্য কথা নয়। বিষয়ের সংজ্ঞা থেকে বিষয়ের গভীরে গিয়ে নাড়ি নক্ষত্র তুলে দেখান, মস্তিস্কের কোষে কোষে ঢুকিয়ে দেন সে বিষয়ের আদ্যোপান্ত। নাসিরাবাদ কলেজের বাংলার অধ্যাপক তিনি। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে মূল্যবান সব বই লিখেছেন। ঘরের বাইরে তাঁর একটিই পোশাক, শাদা ধুতি পাঞ্জাবি। ধুতি পরা লোকদের লোকে খুব সহজে হিন্দু বলে বিচার করে। অথচ যতীন সরকারের মত অসাম্প্রদায়িক বাঙালি এ দেশে খুব কমই আছেন। আপাদমস্তক নাস্তিক তিনি। খাঁটি কমুনিস্ট। ধুতি তাঁর প্রিয় পোশাক বলেই ধুতি পরেন। রবীন্দ্রনজরুলসুকান্ত জয়ন্তীতে পাবলিক লাইব্রেরির অনুষ্ঠানে তাঁর দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তব্য শুনেছি। তিনি প্রায়ই যে কবিকে বেছে নেন প্রশংসা করার জন্য, তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। অবলীলায় নেত্রকোণার আঞ্চলিক সূরে কথা বলে যাচ্ছেন। জীবন যাপন করছেন অতি সাধারণ, দিন এনে দিন খাওয়া লোকদের মত। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর মত এমন ত্যাগী হওয়া আমি জানি, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটি গাড়ি পেলে রিক্সা ছেড়ে গাড়িতে উঠব, যতীন সরকার গাড়িতে উঠবেন না, রিক্সাও নেবেন না, পায়ে হেঁটে পার হবেন পথ। ধন দৌলত বিলাস ব্যসন ছেড়ে নির্লোভ হওয়ার কথা বলা যত সহজ, জীবনে অভ্যেস করা তত সহজ নয়। তবে এই আদর্শকে আজও সম্মান করা হয়, আজও এ শহরের লোকেরা যতীন সরকারকে দেখলে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়, আর্শীবাদ কামনা করে। তবে একজনই একবার দেখেছি মোটে ফিরে তাকাননি। তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঢাকায় এসেছিলেন, সৈয়দ শামসুল হক শক্তিকে প্রস্তাব করলেন ময়মনসিংহে যাওয়ার, শক্তি রাজি, একদিনের নোটিশে তিনি শক্তিকে নিয়ে ময়মনসিংহে চলে এলেন। ফোনে খবর জানিয়ে দিয়েছিলেন ইয়াসমিনকে। আমি তখন ঢাকায়। সৈয়দ হক আমাকে ঢাকা থেকে তুলে নিয়েছেন গাড়িতে। সকাল থেকে ইয়াসমিন বাড়িঘর গুছিয়ে ঝা তকতকে করে রেখেছে। বড় কবি সাহিত্যিকের নাম শুনলে দাদা আবার বরাবরই খুব বিগলিত। কই মাছ থেকে শুরু করে বড় বড় চিংড়ি, ইলিশ, রুই সব তিনি কিনে আনলেন নতুন বাজার থেকে। মা রান্না করলেন। খাবার ঘরে দাদার বিশাল খাবার টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হল খাবার। বিস্তর খাওয়া দাওয়া হল সেদিন দুপুরবেলা। বিকেলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য যতীন সরকার আর ছড়াকার প্রণব রায়কে খবর পাঠিয়ে আনিয়েছি বাড়িতে। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর সৈয়দ হক কী, কেমন আছেন? এই বাক্যটিই শুধু আওড়েছিলেন তিনি। শক্তি সৌজন্য করেও দুটো কথা বললেন না। সৈয়দ হক আর শক্তি নিজেদের মধ্যেই কথা বলে গেলেন। যতীন সরকার আর প্রণব রায় চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে চা বিস্কুট খেয়ে কিছু করার নেই বলে টেবিল থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা টেনে নিয়ে চোখ বুলিয়ে শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন। চমৎকার সাহিত্যের আড্ডা জমানোর উদ্দেশ্যটি আমার সম্পূর্ণই বিফলে গেল। শক্তি সারাক্ষণই বড় বড় ঢেঁকুর তুলছিলেন। সম্ভবত গত রাতে মদ্যপান অতিরিক্তই হয়েছে। কী জানি মদ্যপানে এরকম উদ্ভট রকম ঢেঁকুর বেরোয় কী না! মদে অভ্যেস নেই, জানি না। শক্তিকে খাতির যত্ন করে খাইয়ে দাইয়ে শশিকান্ত মহারাজার বাড়ি আর সত্যজিৎ রায়ের ঠাকরদার ইশকুলটি দেখিয়ে সন্ধেবেলা হাসিমুখে বিদেয় দেওয়া হল। দাদা কৃপা না করলে মুশকিল ছিল। হাড়কেপ্পন হলেও কবি সাহিত্যিকদের বেলায় উদার হতে দ্বিধা করেন না দাদা । একবার যখন হুমায়ূন আহমেদ ময়মনসিংহ শহরে আমার বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে ঠিকানা জানেন না, কিছু না, আমার লেখা পড়ে তাঁর মনে হয়েছে আমি ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে একটি লাল রঙের বাড়িতে থাকি, এবং তার মনে হওয়াকে অনুসরণ করে পাড়ের অনেক বাড়ির কড়া নেড়ে ও বাড়িতে আমি থাকি কি না জিজ্ঞেস করে, থাকি না জেনে, রাস্তায় বেরিয়ে রাস্তার লোকদের জিজ্ঞেস করে করে অবকাশে এসে কড়া নেড়েছেন— চোখের সামনে লেখক হুমায়ূন আহমেদকে দেখে দাদা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। অনেকক্ষণ কোনও কথা ফোটেনি মুখে, তারপর, এক দমে ‘বসেন বসেন, দুপুড়ে কী খাবেন বলেন, মাছ পছন্দ কড়েন তো! আমাড় ওয়াইফ ড়ান্না কড়বে, খুব ভাল ড়ান্না করে। ইস, আগে জানলে তো আমার বন্ধু বান্ধবদেড় খবড় দিতে পাড়তাম’ বলে তক্ষুনি দৌড়ে বাজারে চলে গেলেন বড় বড় তাজা মাছ কিনে আনতে। খেতে খেতে হুমায়ূন আহমেদ গল্প বললেন, অন্যের গল্প নয়, নিজের গল্পই বললেন, সে শুনে হেসে পেট ফাটে দাদার, আমাদেরও। যে গল্প বলতে ভাল পারে, সে ভাল গল্প লিখতে পারে, এরকম একটি ধারণা দাদার জন্মে। আমি যদিও গল্প বলতে একেবারেই জানি না, কিন্তু বেশ কটা গল্প লিখে ফেলেছি এরমধ্যে। গল্পগুলো দৈনিক সংবাদের মেয়েদের পাতা বিভাগে পাঠিয়ে দেখেছি ঝটপট সব ছাপা হয়ে গেছে। মেয়েদের পাতার ধারণাটি আমার একেবারেই পছন্দ হয় না। মেয়েদের পাতার মত ছেলেদের পাতা বলে কোনও বিভাগ থাকে না পত্রিকায়। মেয়েদের আলাদা করে দেওয়া হয়, শিশুদের যেমন আলাদা করা হয়। মেয়ে, শিশু, পঙ্গু বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জন্য সবসময়ই সবকিছু আলাদা। এদের, আমি নিশ্চিত, দুর্বল বলে ভাবা হয়। সাহিত্যের পাতার জন্য গল্প পাঠালে যেহেতু আমি গল্প লেখক বলে পরিচিত নই, আমার গল্প মুড়ির ঠোঙার মত কুঁচকে ফেলে দেওয়া হয় হাবিজিবি কাগজের ঝুড়িতে।
এরশাদকে ক্ষমতাচ্যূত করতে রাজনৈতিক জোটের সভা চলছে , মিছিলে কাঁপছে নগরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ছাত্রছাত্রী সংগঠনও বড় ভূমিকা পালন করছে এই আন্দোলনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিছিলের ওপর ট্রাক চালিয়ে দিয়ে অনেককে হত্যা করেছে এরশাদের পুলিশবহিনী। এখনও রক্তের দাগ মোছেনি ওই এলাকা থেকে। সাংস্কৃতিক জোটও নিরলস অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে বিক্ষোভের, প্রতিবাদের। গাঢ় অন্ধকারে নিরাশার খরস্রোতা নদীতে সাঁতরে সাঁতরে আশার একটি ক্ষীণ আলোর দিকে যেতে থাকি। এই আলো কি সত্যিই আলো, নাকি মরীচিকা! যতীন সরকার আগামীর দিকে তাকিয়ে আছেন, সমাজতান্ত্রিক দল ক্ষমতায় এলে, তাঁর বিশ্বাস, এরশাদের এই পারলৈাকিক মুলোকে পরলোকে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু কবে ক্ষমতায় আসবে ওই দল! দলটি জামাতে ইসলামির চেয়েও দিনে দিনে ছোট আকার ধারণ করেছে। কমরেড ফরহাদ মারা গেলে বিশাল জানাজার আয়োজন হল ইসলামি নিয়মে। কমিউনিস্টরাই যদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে, হোক না সে লোক দেখানো, বেরোতে না পারে, তবে বাকি দলগুলো কী করে বেরোবে! ধর্ম এমনই এক সর্বনাশা জিনিস, এটিকে না মানো ক্ষতি নেই, কিন্তু এটিকে দূর করতে গেলেই গোল বাঁধে। অশিক্ষা আর অজ্ঞানতার কারণে মানুষের ভেতরে একটি অন্ধবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। এই বিশ্বাস কোনও যুক্তি মানে না। মুক্তবুদ্ধিকে পুরোয়া করে না। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে যদি বিদেয় না করা হয়, তবে দেশটি হয়ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হতে সময় নেবে না। ধর্ম হল কর্কট রোগের মত, একবার পেয়ে বসলে একের পর এক ধ্বংস করতে থাকে হাতের কাছে যা পায় তা-ই। এর কোনও নিরাময় নেই। সুস্থতার দিকে কিছুতে মুখ ফেরাতে দেয় না এই রোগ। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের কারণে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ধর্ম বিশ্বাসী মানুষকে অথবা ধর্মে বিশ্বাস না করলেও যারা ওই ধর্মাবলম্বীদের সন্তান, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকতে হবে। কেউ যদি ইসলামের প্রেরণায় আল্লাহর আদেশ পালন করে সাচ্চা মুসলমান হতে চায়, তবে পবিত্র গ্রন্থ কোরান থেকে খুব সহজেই দীক্ষা নিতে পারে যেখানে লেখা ইহুদি আর খিস্টানদের সঙ্গে অর্থাৎ বিধর্মীদের সঙ্গে কোনওরকম বন্ধুত্ব না করার, করলে তাদেরও আল্লাহ ওই বিধর্মীদের সঙ্গে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। কেবল এই নয়, যেখানে বিধর্মী পাও, ধ্বংস কর, খতম কর। যেখানেই অবিশ্বাসী পাও, কেটে ফেলো এক কোপে বাম হাত আর ডান পা, আরেক কোপে ডান হাত আর বাম পা। মুসলমানরাই যে খুব সুখে থাকবে তা নয়। মেয়েদের ওপর চলবে ধর্মের বুলডোজার। বুলডোজারের তলায় পড়ে মেয়েরা আর মেয়ে থাকবে না, খণ্ড খণ্ড মাংসপিণ্ডে পরিণত হবে।
যেমন রক্তের মধ্যে জন্ম নেয় সোনালি অসুখ,
তারপর ফুটে ওঠে ত্বকে মাংসে বীভৎস ক্ষতরা।
জাতির রক্তে আজ তেম্নি দেখ দূরারোগ্য ব্যাধি
ধর্মান্ধ পিশাচ আর পরকাল ব্যবসায়ী রূপে
ঘউ²মশ উঠছে ফুটে ক্ষয়রোগ, রোগের প্রকোপ।
ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃণ্য চতুরতা,
মানুষের পৃথিবীকে শতখণ্ডে বিভক্ত করেছে
তারা টিকিয়ে রেখেছে শ্রেণীভেদ ঈশ্বরের নামে।
ঈশ্বরের নামে তারা অনাচার করেছে জায়েজ।
হা অন্ধতা! হা মুর্খামি! কতদূর কোথায় ঈশ্বর!
অজানা শক্তির নামে হত্যাযজ্ঞ কত রক্তপাত,
কত যে নির্মম ঝড় বয়ে গেল হাজার বছরে!
কোন সেই বেহেস্তের হুর আর তহুরা শরাব?
অন্তহীন যৌনাচারে নিমজ্জিত অনন্ত সময়
যার লোভে মানুষও হয়ে যায় পশুর অধম!
আর কোন দোযখ বা আছে এর চেয়ে ভয়াবহ?
ক্ষুধার আগুন সে কি হাবিয়ার চেয়ে খুব কম??
সে কি রৌরবের চেয়ে নম্র কোনও নরম আগুন?
ইহকাল ভূলে যারা পরকালে মত্ত হয়ে আছে
চলে যাক তারা সব পরপারে বেহেস্তে তাদের।
আমরা থাকব এই পৃথিবীর মাটি জলে নীলে।
দ্বন্দ্ব ময় সভ্যতার গতিশীল স্রোতের ধারায়
আগামীর স্বপ্নে মুগ্ধ বুনে যাবো সমতার বীজ।
একদার অন্ধকারে ধর্ম এনে দিয়েছিল আলো
আজ তার কঙ্কালের হাড় আর পচা মাংসগুলো
ফেরি করে ফেরে কিছু স্বার্থান্বেষী ফাউল মানুষ—
রুদ্র ক্ষেপেছে। কবিতার মধ্যে সে ফাউল শব্দটি ব্যবহার করেছে। মুখের শব্দ অবলীলায় পুরে দিয়েছে কবিতায়। এমনিতে সে প্রচুর গালাগাল দিয়ে কবিতা লিখে যাচ্ছে । কিন্তু ফাউল শব্দটি আমাকে খানিকটা আড়ষ্টতা দিলেও শেষ দুটি স্তবক বারবার আওড়াই – সৃষ্টির অজানা অংশ পূর্ণ করে গাল গল্প দিয়ে
আফিম তবুও ভাল, ধর্ম সে তো হেমলক বিষ।
কাছে থাকলে তার সঙ্গে আমার একদফা তর্ক হয়ে যেত। কিছুতেই আমি মেনে নিতে পারি না ধর্ম কোনও আলো এনেছিল কোনও কালে। অন্ধকার ছাড়া আর কিছু পৃথিবীতে ছড়ায়নি ধর্ম। মানুষের অজ্ঞানতা আর মৃত্যুভয় থেকে জন্ম নিয়েছে ধর্ম। একেশ্বরবাদী পুরুষেরা ধর্ম তৈরি করেছে তাদের আনন্দের জন্য, ইহলৌকিক সুখভোগের জন্য। ইসলামের ইতিহাস বলছে আরবের লোকেরা গুহায় বাস করত, কন্যা জন্ম নিলে জীবন্ত কবর দিত আর সেই দুরবস্থার অবসান ঘটিয়েছেন মোহাম্মদ। দুরবস্থা, আমার যা বিশ্বাস, আগের চেয়ে বেশি এসেছে ইসলাম আসার পর। আগে মেয়েরা বাণিজ্য করত, যুদ্ধে অংশ নিত, নিজের পছন্দমত বিয়ে করত, তালাকও দিত স্বামীদের। মোহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজা ব্যবসায়ী ছিলেন, মোহাম্মদ ছিলেন তাঁর তিন নম্বর স্বামী, বয়সেও তাঁর অনেক ছোট ছিলেন। মেয়েদের জ্যান্ত পুঁতে ফেললে তো মেয়ের সংখ্যা কম হওয়ার কথা। এই যে এত গুলো বিয়ে করত পুরুষেরা, এত মেয়ে কোথায় পেত তবে! মেয়ে পুঁতে ফেললে তো মেয়ের অভাব হওয়ার কথা। তা কিন্তু হয়নি। আরবের লোকেরা স্ফূর্তিতে আমোদে দিন কাটাতো, খেতো, পান করত, বিশ্বাস করত এই জীবনের পরে আর কোনও জীবন নেই, এই জীবনেই যত আনন্দ আছে করে নিত। এই বিশ্বাসের ওপর ধ্বস নামালেন মোহাম্মদ। নিজের সৃষ্ট এই ধর্মকে ক্ষমতা দখল করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি। নিদ্বির্ধায় মানুষ খুন করে, ভিন্ন গোত্রের লোকদের রক্তে স্নান করে, ভিন্ন ধর্মের মানুষকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে, ইহুদি এলাকায় নিজের সৈন্য নামিয়ে দিয়ে তাদের সম্পদ লুঠ করে মেয়েদের ধর্ষণ করে তিনি বিজয় নিশান উড়িয়ে দিলেন। এই ধর্ম কখনও তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যপার ছিল না, ছিল প্রথম থেকে শেষ অবদি, রাজনৈতিক। ইহলৌকিক কোনও আনন্দ থেকে নিজেকে তিনি বঞ্চিত করেনি। যখন যা ইচ্ছে হয়েছে, করেছেন। দোহাই দিয়েছেন আল্লাহর। কাউকে খুন করে এসে বলেছেন আল্লাহ তাঁকে খুন করতে বলেছেন, তাই করেছেন। আল্লাহর আদেশের ওপর যে কোনও কথা বলা যাবে না তা আগে ভাগেই অবশ্য বলে রেখেছিলেন। হারেমের এক ডজনেরও বেশি স্ত্রীর সঙ্গে কাটানোর জন্য মোহাম্মদ রাত ভাগ করে নিয়েছিলেন। স্ত্রী হাফসার সঙ্গে যে রাতটি তাঁর কাটাবার কথা, সেদিন তিনি একটি কাণ্ড ঘটিয়েছিলে। সে দিন হাফসা বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগে বাড়ি ফিরে দেখেন শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বন্ধ কেন? ঘরে কে? ঘরে তাঁর পয়গম্বর স্বামী, আল্লাহর পেয়ারা নবী, মোহাম্মদ, মারিয়া নামের এক ক্রীতদাসীর সঙ্গে সম্ভোগে রত। হাফসা রেগে আগুন হয়ে হারেমের বাকি বউদের এ কথা জানিয়ে দিলেন। নিজের দোষ ঢাকতে মোহাম্মদ আকাশ থেকে আল্লাহকে নামালেন, বললেন, এ তাঁর নিজের ইচ্ছেয় ঘটেনি, ঘটেছে আল্লাহর ইচ্ছেয়, আল্লাহর হুকুম তিনি পালন করেছেন, এর বেশি কিছু নয়। বাংলায় একটি কথা আছে, চুরি আবার সিনা জুড়ি। ব্যপারটি এরকমই। দোষ করার পর কোথায় একটু নতমস্তকে দাঁড়িয়ে নম্রস্বরে কথা বলবেন স্ত্রীদের সঙ্গে, তা নয়, বরং উঁচু গলায় সাবধান বাণী দিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে, আল্লাহ নাকি তাঁকে বলেছেন, ‘যদি তুমি তোমার কোনও স্ত্রীকে তালাক দাও, তবে আল্লাহ তোমার জন্য আরও সুন্দরী, আরও সহনশীল, আরও পবিত্র, আরও নত, আরও লজ্জাবতী, আরও বিশ্বস্ত কুমারী বা বিধবা মেয়ে দেবেন বিয়ে করার জন্য।’ নিজের ছেলের বউ জয়নবকে বিয়ে করেও মোহাম্মদ তাঁর অপকর্মকে জায়েজ করেছেন আল্লাহর ওহি নাজেল করে, আল্লাহ নাকি তাঁকে বলেছেন তাঁর ছেলের বউকে বিয়ে করার জন্য। মোহাম্মদের অল্পপবয়সী সুন্দরী এবং বিচক্ষণ স্ত্রী আয়শা চমৎকার একটি কথা বলেছিল, বলেছিল, ‘তোমার প্রভুটি তোমার সব শখ মেটাতে দেখি খুব দ্রুত এগিয়ে আসেন।’ এই আয়শার দিকে তাঁর বন্ধুরা তাকাতো বলে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে নিজের স্ত্রীদের পর্দার আড়াল করলেন, এরপর ধীরে ধীরে সব মুসলিম মেয়ের শরীরে বাড়তি কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়ার আইন করলেন। ইসলাম নাকি মেয়েদের মর্যাদা দিয়েছে খুব। এই হল মর্যাদার নমুনা। আল্লাহর গমগমে আওয়াজ ভেসে আসে সাত আসমানের ওপর থেকে, ‘পুরুষের অধিকার আছে নারীর ওপর আধিপত্য করার, কারণ আল্লাহ পুরুষকে নারীর চেয়ে উন্নততর মানুষ হিসেবে তৈরি করা করেছেন এবং পুরুষ তার ধন সম্পদ ব্যয় করে।’
কী বলবা এই হল আমাদের পয়গম্বর ব্যাটার চরিত্র, আর তার জোব্বার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আল্লাহ নামের ধোঁকা। এই ইসলামকে পৃথিবীর কোটি কোটি বুদ্ধু আজও টিকিয়ে রাখছে, এর পেছনে আর কিছু না, আছে রাজনীতির খেলা।
বাংলাদেশের অবস্থাও তথৈবচ। তরী ডুবছে এরশাদের তাই উপায়ান্তর না দেখে ইসলাম কে আঁকড়ে ধরে তিনি কূলে ভিড়তে চাইছেন।
ঝুলিয়ে দিয়েছে সম্মুখে এক পারলৌকিক মুলো,
ভীতি ও লালসা নাকের ডগায় কেবলি ওড়ায় ধুলো। .
এইবার চোখে পরে নাও কালো অন্ধত্বের ঠুলি,
যে যত অন্ধ তার তত বেশি বিশ্বাসী বলে নাম।
বিশ্বাস কর, তাহলেই হবে, পেয়ে যাবে রোশনাই।
এই বিশ্বাসে চোখ দুটো খুলে ছুঁড়ে দাও ইহকালে,
আর মগজের সচেতন কোষে তালাচাবি এঁটে দাও।
এই তো সাবাস! এখনি তুমি প্রকৃত ঈমানদার।
০৬. অন্য ভূবন
১৯৮৯ সালে অনেক কিছু ঘটে। অনেক ভাল কিছু, অনেক মন্দ কিছু । কিছু ঘটে আবার ভালও নয়, মন্দও নয়। সকাল প্রকাশনী থেকে গাঁটের পয়সা খরচ করে নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে নামে নিজের একটি কবিতার বই বের করা পড়ে ভালও নয় মন্দও নয় তালিকায়। আজকের এই সকাল কবিতা পরিষদ গড়ার আগে সকাল নামে একটি প্রকাশনী গড়েছিলাম। প্রকাশনীর প্রথম বই যেটি বের করেছিলাম, সেটি কবি আওলাদ হোসেনের কাব্যনাট্য। আওলাদ হোসেনের কথা বলতে গেলে সময় দুবছর পিছিয়ে নিতে হয়। তখন সবে চাকরি হয়েছে ময়মনসিংহ শহরে। নকলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে দু সপ্তাহের মাথায় যাদুর মত বদলি হয়ে ময়মনসিংহ শহরে। কলেজের বন্ধুবান্ধবীরা নতুন চাকরিতে দেশের আনাচ কানাচে ছড়িয়ে গেছে। রুদ্র চিংড়ির ঘের নিয়ে ব্যস্ত মোংলা বন্দরে। কদাচিৎ ঢাকায় ফেরে।
তুমি যখন একা, তুমি যার তার সঙ্গে মেশো। তুমি আওলাদ হোসেনের সঙ্গে মেশো। আওলাদ হোসেনকে বড়জোর তুমি দুবার দেখেছো এর আগে, ঢাকায়। আওলাদ কবিতা লেখেন। কবিতা তুমি ছেপেছোও তোমার সেঁজুতি পত্রিকায়। রুদ্র পাঠিয়েছিল বেশ কিছু তরুণ কবির কবিতা, আওলাদ তার মধ্যে একজন। আওলাদের বাড়ি সিরাজগঞ্জে। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে বিসিএস পাশ দিয়ে রুদ্রর বেশ কিছু বন্ধু, কবিতা বা গল্প লেখায় ইতি টেনে, লম্বা চুলের সর্বনাশ ঘটিয়ে ভদ্র কাট কেটে, স্যুটেড বুটেড ক্লিন শেভড হয়ে, মদ গাঁজা ভাংএর দুর্গন্ধ দূর করে মুখে গম্ভীর গম্ভীর ভাব এনে রীতিমত ভদ্রলোক সেজে ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়েছেন। ইকতিয়ার চোধূরী, কামাল চৌধুরী, আওলাদ হোসেন, মোহাম্মদ সাদিক, ফারুক মইনুদ্দিন..। তুমি যখন সার্কিট হাউজের মাঠে সকালবেলা আন্তঃ জেলা খেলা প্রতিযোগিতায় গেছো, খেলা দেখতে নয়, চিকিৎসা করতে খেলতে গিয়ে চোট লাগা খেলোয়ারদের, তখন পেছন থেকে কেউ একজন তোমাকে ডাকল। কে ডাকল দেখতে যেই না ঘাড় ঘোরালে, দেখলে মিষ্টি মিষ্টি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকা স্যুটেড বুটেড পরিপাটি চুলের একটি লোক। তাকে তুমি চিনতে পারো। শ্রীমান আওলাদ হোসেন।
আপনি এখানে?
হ্যাঁ, আমি তো এখানে চাকরি করি। তথ্য অফিসার হয়ে এই কিছুদিন হল এই শহরে এসেছি। তা আপনার খবর কি? রুদ্র কোথায়, কেমন আছে?
আমি এখানে চাকরি করছি। রুদ্র কোথায়, কেমন আছে, জানি না।
আওলাদ হোসেন গুলকিবাড়িতে তাঁর তথ্য অফিসে তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে দু গাল হাসলেন।
এরপর ইয়াসমিনকে নিয়ে প্রতিদিনকার অভ্যেসমত রিক্সা করে শহর চক্কর দিতে দিতে কোনও এক বিকেলবেলা গুলকিবাড়িতে আওলাদ হোসেনের তথ্য অফিসে ঢুঁ দিয়ে এসো। বড় একটি মাঠ নিয়ে হলুদ একটি একতলা বাড়ি। আওলাদ হোসেন অফিসের খাতাপত্তর গুটিয়ে রুদ্রর সঙ্গে তোমার সম্পর্কের সমাপ্তির কথা শুনলেন। নিজের কথা বলতে তাঁর কবিতার কথাই বললেন বেশি। কাব্য নাট্য লিখেছেন। সেটি নিয়ে তিনি খুব আশাবাদী। তিনি যে করেই হোক এটি ছাপতে চান। রুদ্র আওলাদ হোসেনের কবিতার খুব প্রশংসা করত। নিশ্চয়ই ভাল লিখেছেন তিনি। ডাক্তারির বাইরে আর কিছু করার না থাকলে তুমি তাই কর, একটি কবি-সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভাবো, কবিতা পত্রিকা বের করার ইচ্ছে বুদবুদ করে, এমনকি পুস্তক প্রকাশনার কাজেও হাত দিতে হাত নিশপিশ করে। তুমি এখন উপার্জন কর, মাস গেলে মাইনে পাও, বাপের হোটেলে থাকছ, খাচ্ছ, নিজের টাকা পয়সা খরচ হতে থাকে শিল্প সাহিত্যের সেবায়। আহ, যেন শিল্প সাহিত্য কোনওরকম অসুস্থ ছিল যে তোমার সেবা প্রয়োজন! রোগীর সেবা কর হে বাপু, সাহিত্য বাদ দাও। বাদ দাও বললে বাদ দেওয়া যায় না। পুরোনো শখের শেকড় নতুন ঘটির জল পাচ্ছে। জল পাচ্ছে বলে ঢুঁ মেরে একদিন আওলাদ হোসেনের শখের কাব্য নাট্য নিয়ে জমান প্রিন্টার্সে দিয়ে এসো। আওলাদ হোসেন কথা দেন তিনিই বই বিক্রির ব্যবস্থা করবেন। কাব্য নাট্যটির আগা গোড়া কিছুই না বুঝে তুমি দিব্যি বই বের করে দিলে। তোমার প্রকাশনীর নাম সকাল। সকাল বলে এখন কেউ তোমাকে ডাকে না আর। তুমিই নিজেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ সকাল বলে ডেকে ওঠো। এই সকালে কোনও রোদ নেই। মেঘ মেঘ অন্ধকারে ডুবে আছে তোমার সকাল। সকাল প্রকাশনী থেকে বন্দী দেবতা ছেপে বের করলে নিজে প্রুফ দেখে, গাঁটের পয়সা খরচা করে। আওলাদ হোসেন বলেছিলেন, দুশ বই তিনি নিজেই কিনে নেবেন। কোথায়! দুশ বই আওলাদ হোসেনকে দিলে, তিনশ বই তোমার খাটের তলায়। রুদ্র ময়মনসিংহে বেড়াতে এলে তাকেও কিছু বই দিলে বিক্রি করতে, আওলাদ হোসেনের হলুদ আপিস-বাড়িতে নিয়ে গেলে রুদ্রকে, দু বন্ধুর দেখা করাতে। কিন্তু দেখা তো হল, দেখা হয়ে রুদ্র কি মোটেও সুখ পেয়েছে! পায়নি। বরং সে ঢাকায় ফিরে গিয়ে ইতর নামে ইতরের মত একটি গল্প লিখেছে। সেই ইতরে সে সন্দেহ করেছে যে তুমি যার তার সঙ্গে শুয়ে বেড়াচ্ছে!, আওলাদ হোসেনের সঙ্গেও তোমার সেরকম সম্পর্ক। আসলে তুমি জানো, তুমি কারও সঙ্গে শোওনি। তুমি নিজে জানো যে আওলাদকে নিতান্তই একজন বন্ধু ছাড়া অন্য কোনও ভাবে তুমি দেখ না। তুমি কখনও কল্পনাও করোনি আওলাদের সঙ্গে এই বন্ধুত্বের বাইরে তোমার আর কোনও রকম সম্পর্কের কথা। বরং আওলাদকে বন্ধু বলতেও দিনদিন তোমার আপত্তি হচ্ছে, তাঁর অদ্ভুত আচরণ যে তুমি লক্ষ্য করছ না এমন নয়, করছ। লোকটি উদাসীন, আবার উদাসীনও নয়। কী এক দুর্ভেদ্য ঘোরের মধ্যে থাকেন তিনি। কখনও অনর্গল কথা বলেন, কখনও কোনও কারণ ছাড়াই হেসে ওঠেন, হারমোনিয়ামে মরমিয়া সব সঙ্গীতের সূর তোলেন, আবার কখনও একেবারে চুপ, কোনও কিছুই তাঁর নিমগ্নতা ভাঙতে পারে না। এই আছেন তিনি, এই নেই। আপিসের গাড়ি করে দূর দূরান্তে চলে যাচ্ছেন। গাড়ির চালককে রাতভর খাটাচ্ছেন, কখনও আবার খুব হাসিমুখে চালকের পকেটে টাকা গুঁজে ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন। এক আওলাদ হোসেনের অনেকগুলো চরিত্র। কোনটি আসল, তা তুমি বুঝতে পারো না। ক্রমে ক্রমে তুমি আবিষ্কার করছ যে শম্ভুগঞ্জের এক পীরের কাছে তিনি ঘন ঘন যাচ্ছেন, পীরের সংসারে টাকা পয়সা ঢালছেন, পীরের সঙ্গে বসে গাঁজা খাচ্ছেন। তুমি লক্ষ্য করছ যে আপিসে লোকটি দিন দিন অপ্রিয় হয়ে উঠছেন। নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে মোটেও সম্পর্ক মধুর রাখতে পারছেন না তিনি। আওলাদ হোসেনের আপিসের সমস্যা তুমি সমাধান করতে পারো না, কিন্তু একটি সমস্যার সমাধান করতে চাইলে, যখন তাঁর রাঁধা বাড়া করার জন্য ষোল বছরের মরিয়মের সঙ্গে সত্তর বছরের এক বুড়োর বিয়ে ঠিক করলেন তিনি। বুড়োটি আপিসেই পিয়নের কাজ করে। আওলাদ হোসেনের বক্তব্য দুজনে চুটিয়ে প্রেম করছে, করছে যখন, তখন তিনি ধুমধাম করে বিয়ে দেবেন। চাইলেও তোমার পক্ষে বিয়েটি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। মরিয়মকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে তুমি জিজ্ঞেসও করেছো, কী কারণ এই বুড়োকে বিয়ে করার। মরিয়ম হেসেছে, প্রেমিকারা যেমন করে লাজরাঙা হাসি হাসে তেমন করে। তোমার বিশ্বাস হয়নি মরিয়ম আর আবদুল হামিদ নামের ফোকলা বুড়োর মধ্যে কোনও প্রেম ছিল। সম্ভবত বুড়োর কিছু টাকা আছে আর এক টুকরো জমি আছে, তাই সহায় সম্বলহীন মরিয়মের বাবা এই বিয়েতে রাজি হয়েছেন, মেয়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে, এই আশায়। বিয়েতে বাধা দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হল না। নাতির বয়সী মেয়ের সঙ্গে আবদুল হামিদের বিয়ে দেখে এলে, খেয়ে এলে। আওলাদ হোসেনকে তখন থেকে তোমার মনে হয় যেন তিনি কিছু আড়াল করছেন। লোকটি তাঁর রহস্য কোনওদিন ভাঙেন না। ধোঁয়া ধোঁয়া কিছুর আড়ালে তিনি অনড় মূর্তির মত। একদিন তুমি এও জানবে যে আওলাদ হোসেন তাঁর বউকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ছেলে মেয়ে নিয়ে বউ চলে গেছে সিরাজগঞ্জ। অল্প বয়সে চমৎকার গান গাইত এক মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। বাচ্চা কাচ্চাও হয়ে গেছে আর সব বন্ধুদের চেয়ে অনেক আগেই। প্রায়ই যখন তুমি বউ ছেলে মেয়ে কেমন আছে জিজ্ঞেস কর, আওলাদ হোসেন ওদের খবর জানেন না বলে জানিয়ে দেন। তিনি কোনও টাকা পয়সাও পাঠান না ওদের জন্য। তুমি লক্ষ্য কর, ওদের জন্য লোকটির মোটেও কোনও মায়া হয় না। বউ তাঁর অবাধ্য হয়েছিল বলে তিনি শাস্তি দিয়েছেন। তিনি স্বামী, তিনি সে ক্ষমতা রাখেন। তিনি কবি, তিনি ভাবুক, তিনি এই, তিনি সেই। তিনি লাটসাব, তিনি জমিদার। জমিদারের খবর নিতে তুমি আগ্রহ হারাতে থাকো। না দেখা বউটির জন্য তোমার খুব মায়া হতে থাকে। তুমি বউটির কষ্ট অনুভব করতে থাকো। বছর চলে যায়, তুমি সকাল কবিতা পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুললে আর শহরের কবি আর আবৃত্তিকাররা যোগ দিচ্ছে তোমার সংগঠনে, এই সংগঠনে আওলাদ হোসেনকে যুক্ত করতে পারলে মন্দ হয় না, একজন কেউ প্রস্তাব করার পর তুমি খোঁজ নিয়ে দেখলে আওলাদ হোসেন আর ক্লিন শেভড স্যুটেড বুটেড ভদ্রলোক নন। তিনি শম্ভুগঞ্জে পীরের আসরে গাঁজা টেনে টেনে, পীরকে টাকা পয়সা যা ছিল সব দান করে এখন সর্বস্বান্ত। চাকরিটিও গেছে। মাথা পাগল লোক। খালি পায়ে হাঁটেন। ময়লা কাপড়চোপড়। চুল দাড়িতে মুখ ঢেকে গেছে। আরোগ্য বিতানে নেমে তোমার দাদার কাছ থেকে দু পাঁচ টাকা ভিক্ষে চান। তোমার কাছেও এলেন একদিন টাকা চাইতে। মায়া হল বলে দিলে। আওলাদ হোসেন বগলতলায় একটি বড় বাঁধাই খাতা নিয়ে ঘোরেন আর বলেন তিনি চমৎকার একটি কাব্যনাট্য লিখেছেন, এটি ছাপা হলে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে যাবে। আওলাদ হোসেনকে দেখে সত্যিই খুব মায়া হয় তোমার। সিরাজগঞ্জের জমিদারপুত্র আওলাদ হোসেন ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসার থেকে এক বছরের মধ্যে এখন পথের ভিখিরি। যে মানুষ শখ করে নিজের এমন সর্বনাশ করেছে, তুমি কী ইবা করতে পারো তাঁর জন্য! কিছুই না। তুমি সিদ্ধান্ত নাও এই লোকের জন্য তোমার দরজা আর তুমি খুলবে না, লোককে টাকাও আর দেবে না। টাকা পয়সা অন্য খাতে ঢালা বরং ভাল।
ভালও নয়, মন্দও নয় কাজটি করার ভার তারিক সুজাত নেয়। তারিকের অল্প বয়স, তার ওপর বাচ্চা বাচ্চা মুখ। জাতীয় কবিতা পরিষদ গড়ার সময় যে সব তরুণ কবি দিন নেই রাত নেই দৌড়োদৌড়ি করেছে, তারিক সুজাত তাদের মধ্যে একজন। পরিষদ গঠন করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের চৌরাস্তায় মঞ্চ সাজিয়ে বিরাট করে জাতীয় কবিতা উৎসব করার সেই উত্তেজিত উদ্দীপ্ত সময়ে তারিক সুজাত মোজাম্মেল বাবু শিমুল মোহাম্মদ এমন আরও তরুণ কবির সঙ্গে আমার আর রুদ্রর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। রুদ্রর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে যখন, যখন সম্পর্কটি যায় যায় যাচ্ছে যাচ্ছে অথবা গেছে, তখনও এদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হত। মোজাম্মেল বাবু প্রকৌশলী হয়েও কৌশলে প্রকৌশলে পা না বাড়িয়ে শৈলী নামে একটি পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকা বের করছে। শৈলীর আপিস স্টেডিয়ামের দোতলায়। সাহিত্যের নেশায় বৈষয়িক জগত থেকে মুখ ফিরিয়েছে বাবু। ধনী বাবার ছেলে হয়ে মলিন পোশাকে ঘোরাঘুরি করে। তারিক সুজাতও তাই। তারিককে বই ছাপার সব খরচ দফায় দফায় ঢাকা গিয়ে দিয়ে আসি। বইয়ের পঈচ্ছদ করছেন খালিদ আহসান, শুনে খুব ভাল লাগে। চট্টগ্রামে বাড়ি খালিদের। বইমেলার আগে আগে ঢাকা এসে কিছু বইয়ের চমৎকার পঈচ্ছদ করে দিয়ে যান। নিজে তিনি কবিও। বইটি যেদিন আমার হাতে পাওয়ার কথা, সেদিন তো হাতে আসেইনি, মাস চলে যায়, বইয়ের নাম গন্ধও নেই। তারিককেও খুঁজে পাওয়া যায় না। গরু খোঁজার মত খুঁজে যখন পেলাম, বলে দিল বইএর কাজ এখনও শেষ হয়নি। একশ কাজের কাজীকে এ কাজটি দেওয়া মোটেও উচিত হয়নি, বুঝি। বই যখন কাঁচা বেরোলো বাঁধাই ঘর থেকে, তখন ফেব্রুয়ারির বইমেলার শেষ দিকে। একুশে ফেব্রুয়ারিও পার হয়ে গেছে। ছোটদার বাড়ির খাটের তলায় বইয়ের বাণ্ডিলগুলো রেখে দিই। কিছু বই মেলার কিছু দোকানে সদলবলে দিই বটে, দ্বিধায় সংকোচে আমি বইয়ের দোকানগুলোর আশপাশ দিয়ে হাঁটি না, যদি দেখি যে পাঁচটি বই দোকানে ছিল, সেই পাঁচটিই পড়ে আছে অনাথের মত! বিক্রি যদি কিছু হয় তো হয়েছে। খোঁজও নিই না। টাকা আনতেও দোকানে উঁকি দিই না। মেলার চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে কাটাই। মেলা শেষ হলে বইয়ের বস্তা নিয়ে ময়মনসিংহে ফিরি। গাঙ্গিনাড় পাড়ের কবীর লাইব্রেরী আর পারুল লাইব্রেরীতে বই রেখে আসি যদি কেউ কেনে। কদিন পর পর লাইব্রেরীতে বই কিনতে গিয়ে আমার পড়ে থাকা বইগুলোর দিকে চোখ পড়ে। চোখ ঘুরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরি। এই মনোকষ্ট থেকে নাইম আমাকে উদ্ধার করে। নাইমের সঙ্গে পরিচয় আবু হাসান শাহরিয়ারের মাধ্যমে। শাহরিয়ার ময়মনসিংহে এসেছিল কবিতা অনুষ্ঠানে। শাহরিয়ার ছড়া লেখে, ময়মনসিংহের ছড়াকার আতাউল করিম সফিকের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ ওর। আতাউল করিমই ওকে নিয়ে যায় টাউন হলের বটতলায় সকাল কবিতা পরিষদের প্রতিবাদের কবিতা অনুষ্ঠানে। নিজে সে চমৎকার একটি কবিতা পড়ে অনুষ্ঠানে। তেমন লোক জমেনি বটতলায়। কিন্তু শাহরিয়ার এমনই মুগ্ধ সকালের বৃন্দ আবৃত্তি শুনে যে ঢাকায় গিয়ে স্বরশ্রুতিকে জানায়। স্বরশ্রুতি একটি বড় আবৃত্তি সংগঠন। স্বরশ্রুতি তখন বৃটিশ কাউন্সিলের অডিটোরিয়ামে বিশাল এক অনুষ্ঠান করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দেশের প্রথিতযশা কবিদের এমন কী পশ্চিমবঙ্গের কবিদেরও। একক আবৃত্তি, বৃন্দ আবৃত্তির জন্য আমন্ত্রণ যাচ্ছে বিভিন্ন শিল্পীর কাছে, গোষ্ঠীর কাছে এপার বাংলায়, ওপার বাংলায়। স্বরশ্রুতির একটি আমন্ত্রণ সকাল কবিতা পরিষদের জোটে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র পাশা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রোজেলিন, শহরের ছোটখাটো চশমাপরা আঁতেল আবৃত্তিকার দোলন, ইয়াসমিন আর আমি আবৃত্তির মহড়ায় মহা উৎসাহে নেমে পড়ি। চলে অবকাশে। সুস্থ রাজনীতি, বৈষম্যহীন সমাজ, সমতা আর সাম্যের স্বপ্ন ঝংকৃত হয় প্রতিটি কণ্ঠে। দল বেঁধে ঢাকা গিয়ে মেয়েরা জামদানি শাড়ি, ছেলেরা সাদা পাঞ্জাবি পাজামা পরে মঞ্চে উঠে যাই। আবৃত্তি করি কোথাও একক, কোথাও দুজন, কোথাও তিন জন, কোথাও সকলে। কারও কোনও ভুল হয় না, কোনও পা কাঁপাকাঁপি নেই কারও। দিব্যি শ্রোতা দর্শকদের হাততালি কুড়িয়ে নেমে আসি মফস্বলের আবৃত্তি-দল। মফস্বলের দল হিসেবে ঢাকায় তেমন দাম পাওয়া যায় না। বরাবরই ঢাকার কবি বা আবৃত্তিকারদের মধ্যে একটু দাদাগিরি ভাব আছেই। দাদাগিরি উড়িয়ে দিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাঠে বসে ঢাকার কবিবন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘ আড্ডা জমিয়ে তুলি। শাহরিয়ার সে মাঠেই পরিচয় করিয়ে দেয় নাইমের সঙ্গে। দেখতে বিচ্ছিরি নাইম। উঁচু দাঁত, উঁচু কপাল। চুলের কোনও ছিরিছাদ নেই। ও কটা চুল এই বয়সেই পাকতে শুরু করেছে। হাড়সর্বস্ব শরীর। হাত পা বাতাসে ছুঁড়ে ছুঁড়ে কথা বলে। হাঁটলে নিতম্ব দোলে। কিলো পঞ্চাশেক ওজনের শরীরে এই এতটুকুন নিতম্ব। নাইম খবরের কাগজ নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকাটি রাজনীতি সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদির পাঁচ মিশেলি পত্রিকা, বেশ নাম করেছে এর মধ্যে। খুব সস্তায় বের করে, পঈচ্ছদও নিউজপ্রিণ্টে। দেশে কয়েক ডজন সাপ্তাহিকী বেরোয়, খবরের কাগজ সবগুলোর চেয়ে অন্যরকম। বড় বড় কবি সাহিত্যিকদের দিয়ে কলাম লেখানো হচ্ছে পত্রিকায়। এরকম একটি সুস্থ সুন্দর পত্রিকার প্রয়োজন ছিল দেশে। পত্রিকার নাম হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নাইমের পরিচয়ও বাড়ছে লেখক অঙ্গনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় বিভাগে পড়াশুনো করা ছেলে হঠাৎ করে কবি সাহিত্যিকদের এমন ঘরের লোক হয়ে যায় না। গুণ আছে বটে বিচ্ছিরি দেখতে ছেলেটির। তারিকের মত নাইমও একশ কাজের কাজী। স্বরশ্রুতি আবৃত্তি সংগঠনের সে সভাপতি জাতীয় কিছু একটা হয়ে বসে আছে, যদিও কবিতা বা আবৃত্তি কিছুরই মাথামুণ্ডু সে জানে না। নাইমের একটি ভাল দিক, সে অকপটে স্বীকার করে যা সে জানে না। তবে যা সে জানে, তা নিয়ে অহংকার তার কম নয়। অহংকার কখনও সুপ্ত, কখনও বিকট রূপে প্রকাশিত। কুমিল্লার আঞ্চলিক সুরে কথা বলা নাইমকে আমার প্রথম দেখায় পছন্দ হওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু পরিচয় থেকে চেনা জানা, চেনা জানা থেকে বন্ধুত্ব হতে খুব বেশি সময় নেয় না। সময় নেয় না কারণ নাইম সিদ্ধান্তই নিয়েছিল আমার সঙ্গে সে যে করেই হোক বন্ধুত্ব করবে। নাইম যা ভাবে তা যে করেই হোক সে করে ছাড়ে। তার যে জিনিসটি আমার ভাল লাগে, তা হল নতুন কিছু করার উৎসাহ। নতুন ধরনের কিছু। প্রতিনিয়ত সে পরিকল্পনা করছে, আর ঝাঁপিয়ে পড়ছে তা বাস্তবায়ন করতে। প্রচণ্ড উৎসাহী, উদ্যমী, ক্লান্তিহীন, কর্মঠ যুবক। শাহরিয়ার, নাইম, আমি প্রায় সমবয়সী। আমাদের আড্ডা জমে ভাল। শাহরিয়ারও ডাক্তারি ছেড়ে এসে মন্দ করেনি, গতি নামে একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা খুলেছে। গতি, শাহরিয়ার বলে, অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের খোরাক জোটাতে, আর মনের খোরাকের জন্য আছে সাহিত্য। দুটোই চলছে ভাল শাহরিয়ারের। শাহরিয়ারের ছড়াকার বন্ধু সৈয়দ আল ফারুকের আছে গার্মেন্টসএর ব্যবসা। নিজের পয়সায় নিজের ছড়ার বই বের করে। শাহরিয়ার আর ফারুক মিলে একসময় ছড়া-পত্রিকা বের করত। সেই জিগরি দোস্ত ফারুকের সঙ্গে শাহরিয়ারের আজকাল বনিবনা হচ্ছে না। বনিবনা না হলে শাহরিয়ারের ধারালো জিভে তাকে খণ্ড খণ্ড হতেই হবে। নাইম আর শাহরিয়ারের মধ্যে অনেক অমিল, কিন্তু একটি ব্যপারে খুব মিল, তা হল যদি কাউকে পছন্দ করে তো তার মত ভাল পৃথিবীতে আর একটিও নেই, সে দেবতা, ভগবান, ঈশ্বর ! আর যাকে অপছন্দ হয়, সে নরকের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম কীট ছাড়া কিছু নয়। এসব আমি তাদের সঙ্গে কেবল কদিনের কথাবার্তাতেই বুঝিনি, দীর্ঘদিন সময় লেগেছে। মাঝে মাঝে কিছু সাদামাটা জিনিসও সময় আমার কিছু বেশিই নিয়ে নেয়। শাহরিয়ারের মাধ্যমে পরিচয় হলেও একসময় শাহরিয়ারের চেয়েই বেশি দেখা হতে থাকে নাইমের সঙ্গে। নাইমের অতি উৎসাহের কারণেই ঘটে সব। শাহরিয়ারের সঙ্গে দেখা কম হওয়ার কারণ শাহরিয়ার নিজেই। একদিন সে আমাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল। গিয়ে দেখি বাড়ি খালি, তার বউ ঢাকায় নেই। খালি বাড়িতে প্রথম ভাল গল্প হল, কিন্তু এরপর শাহরিয়ারকে দেখে আমি অবাক, সে আমার রূপের প্রশংসা করতে করতে আমার গা ঘেঁসে বসে আমাকে জোর করে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছে। ঠেলে তাকে সরিয়ে দিয়েছি বারবার। নিরাপদ দূরত্বে যতবারই বসতে চেয়েছি, ততবারই সে দূরত্ব ঘোঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তার ওই নিরন্তর চেষ্টা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আমার সামান্যতমও আগ্রহ নেই তার ঠোঁটের কাছে নিজের ঠোঁট পেতে দেওয়ার এবং তাকে অনুরোধ করেছি আমাদের সুন্দর বন্ধুত্বটি যেন সে এভাবে নষ্ট না করে ফেলে কিন্তু তারপরও যখন সে হাত বাড়ানো বন্ধ করেনি, অতিষ্ট হয়ে আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে তার বাড়ি থেকে। আমাকে চুমু খেয়ে শাহরিয়ার হয়ত তার বউ মুনিরার কালো ঠোঁটে হযরে আসওয়াদ হযরে আসওয়াদ বলে চুমু খেয়ে পূর্ণ করত পাপী ও সন্তপ্ত প্রেমিকের হজ্ব। নাইমের সঙ্গে এই সমস্যা হয় না। নাইম কখনও কোনও সুযোগ নিতে চেষ্টা করে না, আমরা কোনও খালি ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিলেও না। নাইম আমার একজন ভাল বন্ধু হয়ে ওঠে, ভাল বন্ধু মানেই তো এই যাকে বিশ্বাস করা যায়, যে সুখ দুঃখে পাশে দাঁড়ায়। নাইমের সঙ্গে পুরোনো দিনের গল্প করতে করতে একদিন চন্দনার কথা বলি, চন্দনা কুমিল্লায় থাকে বলতেই নাইম আমাকে তার গাড়িতে তোলে কুমিল্লা যাওয়ার জন্য। ইমদাদুল হক মিলন ভিড়েছিল, মিলনকেও নেওয়া হল। নাইম, মিলন আর আমি ঢাকা ছেড়ে সোজা কুমিল্লা। মিলনকে নিয়ে নাইম একদিন অবকাশে হাজির হয়ে আমাকে চমকে দিয়েছিল। নাইমের স্বভাবে এই চমকে দেওয়া ব্যাপারটি খুব আছে। সেদিন নাইমের এই এক তুড়িতে কুমিল্লা যাওয়ার সিদ্ধান্তটি সত্যিই ভীষণ ভাল লেগেছে। আমিও এরকম, যা মনে হয় করতে, সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলি, কালের জন্য আমার কিছু ফেলে রাখতে ইচ্ছে করে না। কিছু করার আগে ভাবনা চিন্তা করা আমার একদম ভাল লাগে না। কুমিল্লায় চন্দনার শ্বশুর বাড়ি খুঁজে বের করে ঢুকে দেখি একটি ছোট বাচ্চার মা সে, বাড়ির ঘোমটা পরা পূত্রবধূ সে। সেই চন্দনা, আমার চন্দনা, এত কাছের সে, তারপরও কত দূরের। আমি স্পর্শ করি চন্দনাকে, আমার সেই আগের চন্দনাকে, গৃহবধু চন্দনা সে স্পর্শ কতটৃকু অনুভব করে আমি ঠিক বুঝি না। বলি, ‘রাঙামাটি গিয়েছিলাম, ওখানে কেবল তোর কথাই মনে হয়েছে, আমাদের যে কথা ছিল দুজনে রাঙামাটি যাবো, তুই আমাকে সব দেখাবি, সব চেনাবি, কত আনন্দ করব আমরা, মনে আছে!’ বুঝি না সেই কথার কথা চন্দনার আজও মনে আছে কি না। যখন হাতে চাঁদ পাওয়া উচ্ছঅ!সে বলি চল বেরোই, চল কোথাও ঘুরে আসি, চল ময়মনসিংহ যাই, চল ঢাকা যাই। চন্দনা হাসে আমার পাগলামি দেখে। চন্দনা খুব জোরে হাসে না, খুব জোরে কথা বলে না। অসম্ভব এক পরিমিতি বোধ তার এখন। সন্তর্পণে হাঁটে, সন্তর্পণে কথা বলে, চিলেকোঠার গোলাপ বাগানে নিয়ে গোলাপের কথাই বেশি বলে। মিলনের গল্প চন্দনা অনেক পড়েছে, এমনকি ওর ও সজনী গল্পটি পড়ে নিজের নামেই সজনী জুড়েছে, কিন্তু মিলনও চন্দনার জন্য এখন আর কোনও আকর্ষণ নয়। মিলনকে দেখে চন্দনা, খুব শান্ত চোখে দেখে, যেমন করে যে কোনও রহিম করিমকে দেখে। মিলনের সঙ্গে এর পরেও আমার মাঝে মাঝে দেখা হতে থাকে। বন্ধুত্ব মিলনের সঙ্গেও গড়ায়, আপনি থেকে তুমিতে সম্বোধন জলের মত গড়িয়ে যায়।
সাহিত্যিক, অসাহিত্যিক দু জগতেই আমার বন্ধুর সংখ্যা একটু একটু করে বাড়ে। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ডাক্তার সাইদুল ইসলাম, সাহিত্যের কোনও খবর যে কোনওদিন রাখে না, ভাল বন্ধু হয়ে ওঠে। বন্ধুত্বের দুয়োর আমি বন্ধ করে রাখি না। তাই বলে দুয়োরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আছি যে কোনও কাউকে বন্ধু করার জন্য, তা নয়। অনেক সাহিত্যিককে আমি প্রথম আলাপে না হোক দ্বিতীয় আলাপেই খারিজ করে দিয়েছি। হারুন রশিদের কথাই ধরি। সাংঘাতিক প্রতিভা ছেলেটির। সেই সেঁজুতি ছাপার সময় থেকেই হারুনকে চিনি আমি। তার কবিতার রীতিমত ভক্ত ছিলাম। চিঠিতে যোগাযোগ ছিল প্রথম প্রথম, একবার দেখাও করতে এসেছিল, কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কের মত দেখা করতে সে আসতে পারে বটে, কিন্তু দেখা তাকে কে দেবে! আমি মফস্বলের লজ্জাশীলা মেয়ে, দেখা করব, তেমন সাহস আমার ছিল না বলতে গেলে। সেই হারুনই কয়েক বছর পর যখন দিব্যি হুট করে অবকাশে এল, এমন ভঙ্গিতে যে এসেছি আমি, আমার এই দেহখানি তুলে যদি না ধরতে পারো, অন্তত অনুমতি দাও তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ হতে – যেহেতু আমার সঙ্গে রুদ্রর বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, আমি একা, অতল একাকীত্বে আমি ডুবে যাচ্ছি, আমি এখন তার মত সুদর্শন যৃবককে কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারব না। হারুন আমার দিকে প্রেম প্রেম চোখে যতই তাকাতে চায়, আমি চোখ সরিয়ে নারকেল গাছের ঝুলে থাকা ঝুলে থাকা নারকেলের দিকে চেয়ে থাকি, জানালার শিকে চেয়ে থাকি, গত বর্ষায় বজ্রপাতে পুড়ে যাওয়া সুপুরি গাছের মাথার দিকে চেয়ে থাকি, বলার মত কোনও শব্দ খুঁজে পাই না। বরং শব্দ খুঁজে পাই সেওড়াগাছের ভুতের মত দেখতে ফরিদ কবির নামের যে কবিকে হারুন সঙ্গে এনেছিল, তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। ঢাকায় হারুনের বাড়িতে গিয়েও আমাকে আবার সেই অস্বস্তিকর অবস্থায় পেয়েছিল। কিছুতেই হারুনের সঙ্গে আমার সাদামাটা সহজ সম্পর্কটিও হয়নি। এর মানে এই নয়, যাকে আমি বন্ধু বলে মেনে নিলাম, সে আমার আদপেই বন্ধু কোনও, আর যে মানুষকে তুচ্ছ করলাম, হেলায় ফিরিয়ে দিলাম, সে আমার খুব ভাল বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। হারুনের কথা না হয় বাদই দিলাম, হেলাল হাফিজের সঙ্গে সম্পর্ক ওভাবে শেষ হবে ভাবতে পারিনি কখনও। আসলে সম্পর্ক যেমন যেভাবে যে জায়গায় আছে, তার চেয়ে হঠাৎ করে সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিলে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায় সব। হেলাল হাফিজের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেকদিনের। সেঁজুতির জন্য কবিতা চাইতে গিয়ে পরিচয়। প্রায়ই যখন কিছু করার থাকে না, বাড়িতে বসে থাকতেও ভাল লাগে না, প্রেসক্লাবে হেলাল হাফিজের সঙ্গে দেখা করতে যাই। দেখা করতে যাওয়া মানেই তিনি রেস্তোরাঁয় বসাবেন, দুপুরে একজনের বদলে দুজনের খাবার দিতে বলবেন। দুজন ভিড়ের রেস্তোরাঁয় বসে খাবো। আমি কখনও খাবারের পয়সা দিতে চাইলে তিনি কিছুতেই দিতে দেবেন না। কোনও উপহার তার জন্য নিয়ে গেলেও খুব ঠাণ্ডা গলায় বলবেন, তিনি কারও কোনও উপহার নেন না, আমি যেন উপহারটি নিয়ে চলে যাই, নিজে ব্যবহার করি অথবা অন্য কাউকে দিয়ে দিই। তাঁর সঙ্গে আমার কথা যা হয় তার মধ্যে বেশির ভাগই পরিবারের কথা। তিনি জানতে চান আমার বাবা কেমন আছেন, মা কেমন আছেন, দুই ভাই কেমন আছেন, বোন কেমন, এসব। হেলাল হাফিজ একা থাকেন, বিয়ে থা করেননি। একটি পত্রিকায় কাজ করতেন, পত্রিকা উঠে যাওয়ার পর তিনি কোথাও চাকরি বাকরি করেন না, জুয়ো খেলে জীবন কাটান। জুয়োতে তাঁর ভাগ্য খুব ভাল, জেতেন বেশির ভাগ সময়। আমাকে একবার জুয়োর নেশায় পেয়েছিল, তা অবশ্য খুব বেশিদিন টেকেনি। প্রতিরাতে হাসিনার আসলে আপন বোন নকলে ফুপাতো বোন পারভিনের বাড়িতে প্রতি সন্ধায় জুয়োর আসর বসত। বাঘা বাঘা সব খেলোয়ার টাকার তোড়া পকেটে নিয়ে জুয়ো খেলতে আসতেন। পারভিন আর তাঁর খেলোয়ার বন্ধুরা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন কী করে ফ্লাশ খেলতে হয়। শেখানো খেলা খেলতে গিয়ে দেখি এক পশলা দেখা দিয়েই হাওয়াই মিঠাইয়ের মত উবে যায় আমার টাকা। প্রতিবারই মনে হয় বুঝি জিতব আর প্রতিবারই গাদা গাদা টাকা হেরে আসি। বাড়ি ফেরার সময় এমনকী হাতে রিক্সাভাড়ার পয়সাটিও থাকে না। খালি হাতে বাড়ি ফিরে দুটো টাকার জন্য এর ওর কাছে হাত পাততে হয়। আমাকে নিরীহ পেয়ে লোকেরা আমাকে ঠকাচ্ছে এই কথাটি আমার বোঝার সাধ্য ছিল না, কিন্তু বাবার হস্তক্ষেপে দাদা জ্ঞানদান করে করে আমাকে সরিয়েছেন জুয়োর আড্ডা থেকে। তবে ক্রমাগত হারলেও এ কথা স্বীকার আমি করি, উত্তেজনা ছিল খেলায়। টাকা আসে টাকা যায়, কিন্তু টাকা কি সবসময় এরকম উত্তেজক সময় দিতে পারে? পারে না। হেলাল হাফিজের জুয়ো খেলা প্রতিদিনের দশটা পাঁচটা চাকরি করার মত। সংসার বিরাগী একটি মানুষকে এভাবে মানিয়ে যায়। কোনও ঘর কারও ঘর তাঁকে টানে না। সামাজিক নিয়ম কানুনকে য়চ্ছন্দে পাশ কাটিয়ে চলে যান, স্পর্শ করেন না কিছু অথবা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। হেলাল হাফিজ মানুষটির এই অন্যরকম দিকটি আমাকে আকর্ষণ করে তাই এত বেশি। আমিও যদি পারতাম তাঁর মত নিস্পৃহ হতে। যে কেউ পারে না জানি। ঢাকা থেকে যখন তিনি আমাকে ময়মনসিংহে প্রায় প্রতিদিন ফোন করতেন, তখনও আমার মনে হয়নি তিনি আমার শ্রদ্ধাস্পদ দাদা ছাড়া অন্য কিছুতে রূপান্তরিত আদৌ হতে চান। আমার আশঙ্কার সূচনা আমাকে নিয়ে লেখা তাঁর কবিতা আর আমার জন্য একটি নতুন নাম তৈরি করা। তারপর যে মানুষ নিজের ঘর আর প্রেসক্লাবের বাইরে অন্য কোথাও যান না, কোনও বাড়িতে না, কোনও অনুষ্ঠানে না, তিনি কি না পঁচিশে আগস্টে চলে এলেন ময়মনসিংহে, আমার জন্মদিন পালন করতে! ঢাকায় গেলে তিনি একবার ছোটদার বাড়িতেও নিজের সব কৃচ্ছউত!র সঙ্গে যুদ্ধ করে চলে এসেছিলেন, এমনই ছিল তাঁর আবেগ। আবেগে যখনই তিনি প্রেম প্রেম চোখে তাকিয়েছেন আমার দিকে, আমি চোখ সরিয়ে নিয়েছি। যেদিন প্রথম আমার হাতটি নিলেন নিজের হাতে, দ্রুত আমি কেড়ে নিয়েছিলাম নিজের হাতটি, তিনি আবারও সেটি নিয়ে রাখতে চাইছেলেন অনেকক্ষণ তাঁর উষ্ণ হাতে। আমার ভাল লাগেনি, এই রূপে আমি তাঁকে দেখতে চাইনি। বড় বেমানান তিনি, যখন বলেন,
কোনওদিন আচমকা একদিন
ভালবাসা এসে যদি হুট করে বলে বসে
চলো যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই,
যাবে?
আমার চোখে তখন এই হেলাল হাফিজ সেই হেলাল হাফিজ নয়, উনসত্তরে যাঁর একটি কবিতা হাজার মানুষকে উদ্দীপিত করেছে রাজপথের মিছিলে নামতে।
এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়,
এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।
সেই হেলাল হাফিজ যাঁর সংসারহীন উদাসীনতা, যাঁর মৌনতা মগ্নতা আমাকে মুগ্ধ করে। যাঁর কবিতার বিষাদ আমাকে আবৃত করে, তিনি ঠিক সেই মানুষটি নন। আমি খুব ভাল করেই জানি যে হেলাল হাফিজকে আমি আমার প্রেমিক হিসেবে কল্পনা কখনও করিনি। যাঁর মহত্বের পদধূলিতে পুস্পাঞ্জলি অর্পণ করে নিজেকে ধন্য মানি, তিনি যদি সেই শীর্ষাসন থেকে নেমে আমারই ধুলোয় গড়াগড়ি যান, তবে আমার যেমন সব যায়, তাঁরও যায়। তাঁর কাতর করুণ চোখে আমার কুঞ্চিত কুণ্ঠিত দৃষ্টি কালো কালো মেঘ ছুঁড়ে দিতে থাকে। আমার ভেতরে না কল্পনা করা অবিশ্বাস্য রকম বিস্মিত মানুষটি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, মানুষটির কণ্ঠস্বর কঠিন হতে থাকে, নির্দয়তা তার স্বভাবসুলভ নম্রতা ঢেকে দেয়, তাকে অমানবিক করে তোলে, তাকে অমানুষ করে তোলে। সে কঠোর হতে হতে, আরও কঠোর হতে হতে সেই আপাদমস্তক কবিটিকে, নিরীহ সংসারবৈরাগ্য যাঁর অঙ্গে অঙ্গে অথচ গোপনে গোপনে যে প্রচণ্ড এক স্বপ্নচারি মানুষ, ভুল করে একটি ভুল স্বপ্নের গা ছুঁতে গিয়েছিল— বের করে দেয় বাড়ি থেকে।
হেলাল ভাই, আপনি চলে যান, এক্ষুনি চলে যান এখান থেকে।
স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ছিল সে কণ্ঠে, ছিল হতাশা, ছিল কিছুটা ঘৃণাও। রুমালে চোখ মুছতে মুছতে তিনি চলে গেছেন। তাঁর চলে যাওয়ার দিকে ফিরে তাকাইনি আমি, ভেতরে তখনও কঠোর আমিটি আমাকে বারণ করছে তাঁর চলে যাওয়ার দিকে করুণ করে তাকাতে। যে প্রণয় মানুষটিকে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে শিখিয়েছিল, আছি,
বড্ড জানান দিতে ইচ্ছে করে, — আছি,
মনে ও মগজে গুনগুন করে
প্রণয়ের মৌমাছি।
সেই তাঁকেই লিখতে হল
আমারে কান্দাইয়া তুমি
কতোখানি সুখী হইছ,
একদিন আইয়া কইয়া যাইও।
আমার কোনওদিন তাঁরে গিয়া কওয়া হয় নাই, কতখানি সুখী হইছি আমি। কেবল দূর থেকে তাঁর ছোট ছোট পদ্য পড়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। ছোবল তাঁকে আমি দিতে চাইনি। মন দেওয়ার কথাও আমার মনে কখনও আসেনি।
ভালবেসেই নাম দিয়েছি তনা,
মন না দিলে
ছোবল দিও তুলে বিষের ফণা।
তনার সঙ্গে ফণা মিলে যায় বটে, কিন্তু আমি কখনও বিষাক্ত সাপ ছিলাম না যে হেলাল হাফিজের মত নিরীহ নির্জন মানুষকে আমি ছোবল দিতে যাবো। আমি সে যেই হোক, একবার যদি বন্ধুত্ব হয়, কখনও সম্পর্ক নষ্ট করার পক্ষে নই। কিন্তু হেলাল হাফিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার আমার কোনও মুখ রইল না। যদিও ছোবল দেওয়ার কথা বলেছিলেন মন যদি না দিই, কিন্তু আবার রাগ দেখিয়েছেন এ বলেও যে,
যদি যেতে চাও, যাও
আমি পথ হব চরণের তলে
ফেরাবো না, পোড়াবোই হিমের অনলে।
অথবা
তোমার হাতে দিয়েছিলাম অথৈ সম্ভাবনা
তুমি কি আর অসাধারণ? তোমার যে যন্ত্রণা
খুব মামুলী, বেশ করেছো চতুর সুদর্শনা
আমার সঙ্গে চুকিয়ে ফেলে চিকন বিড়ম্বনা।
কিন্তু নরম মনটি এরকম গাল দিয়ে স্বস্তি পেতে পারে না। কতটুকু উদার হতে পারেন তিনি তাও বলেছেন —
আমাকে উষ্টা মেরে দিব্যি যাচ্ছো চলে
দেখি দেখি
বাঁ পায়ের চারু নখে চোট লাগেনি তো!
ইস করেছো কি! বসো না লক্ষ্মীটি
ক্ষমার রুমালে মুছে সজীব ক্ষতেই
এন্টিসেপটিক দুটো চুমু দিয়ে দিই।
এখন যৌবন যার বইটির অসামান্য সাফল্যের পরে অভিমানী কবির দ্বিতীয় বই যে জলে আগুন জ্বলে বেরোচ্ছে। এর পরের বইএর জন্য নাম ঠিক করেছেন তিনি, যদিও কবিতা একটিও লেখা হয়নি, নামটি আমার কানে কানে বলেছিলেন, কার কী নষ্ট করেছিলাম! মাঝখানে অচল প্রেমের পদ্য ধ্রুব এষের আঁকা কার্ডে বেরিয়েছে। ছোট ছোট পদ্যগুলো পড়ে কষ্ট পেয়েছি, কষ্ট পেয়েছি তিনি কষ্ট পেয়েছেন বলে। ওরকম প্রেমে তিনি না পড়লেও পারতেন। কী দরকার ছিল! কী দরকার ছিল কষ্ট পাওয়ার, কষ্ট দেওয়ার! আসলে সংসার বিরাগী হিসেবে সকলে হেলাল হাফিজকে জানলেও আমার মনে হয় তিনি ভেতরে ভেতরে খুব সংসারী একটি মানুষ। তিনি যে মেয়েদের ভালবেসেছেন, তাদের কেউই তাঁকে সত্যিকার ভালবাসেনি। তাই কখনও তাঁর সংসার করা হয়নি, কেউ হয়তো বোঝে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটি স্বপ্ন তিনি লালন করেন। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও আসলে খুব গোছানো মানুষ তিনি। ইস্ত্রি করা সার্ট প্যান্ট পরবেন, চকচকে স্যান্ডেল পরবেন, আর একটি মোটা কাপড়ের ঝোলা থাকবে কাঁধে, ঝোলায় তাঁর কলম, কিছু কাগজ, সিগারেটের প্যাকেট, সবই খুব সুন্দর করে গোছানো। এমন গুছিয়ে তো কিছু আমি কোনওদিন রাখি না। কাঁধে ঝোলা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো দাড়িঅলা কোনও মানুষ দেখলে কবি কবি লাগে, উদাসীন উদাসীন, এলোমেলো অগোছালো মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়। কষ্ট পেতে কেউ কেউ ভালবাসেন, কেউ কেউ সন্ন্যাসী হতে ভালবাসেন। হেলাল হাফিজ তাঁর এককালের প্রেমিকাকে হারিয়ে নিজেই বলেছেন অনেক কষ্টের দামে জীবন গিয়েছে জেনে, মূলতই ভালবাসা মিলনে মলিন হয়, বিরহে উজ্জল। কষ্ট ফেরি করেন তিনি, সেই কতকাল আগে, আমার সঙ্গে যখনও পরিচয় হয়নি, লিখেছিলেন, পড়েছিলেন ফেরিঅলার মত সূর করে, কষ্ট নেবে কষ্ট,
হরেক রকম কষ্ট আছে, লাল কষ্ট নীল কষ্ট.
অনাদর আর অবহেলার তুমুল কষ্ট,
ভুল রমণী ভালোবাসার
ভুল নেতাদের জনসভার
হাইড্রাজেনে দুইটি জোকার নষ্ট হবার কষ্ট আছে,
কষ্ট নেবে কষ্ট?
আর কে দেবে আমি ছাড়া
আসল শোভন কষ্ট
কার পুড়েছে জন্ম থেকে কপাল এমন
আমার মত কজনের আর
সব হয়েছে নষ্ট
আর কে দেবে আমার মত হৃষ্টপুষ্ট কষ্ট!
গোপনে গোপনে ভালবসেন তিনি, যাকে ভালবাসেন, সে ই বোঝে না তিনি যে ভালবাসেন। একাকী বসে বেদনার জাল বোনেন তিনি, জানতে চান ভালবাসার মানুষটি কেমন আছে, যদি চিঠি না লেখে প্রেমিকা, তবে তিনি অভিমান করে বলেন,
..আর না হলে যত্ন করে ভুলেই যেও, আপত্তি নেই।
গিয়ে থাকলে আমার গেছে, কার কী তাতে?
আমি না হয় ভালবেসেই ভুল করেছি ভুল করেছি
নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে
পাঁচ দুপুরে নির্জনতা খুন করেছি, কী আসে যায়!
বোন নেত্রকোণাকে ভালবাসেন তিনি, কিন্তু যান না তিনি নেত্রকোনার কাছে, নেত্রকোনা আছে তাঁর মজ্জার আর মগজের কোষে অনুক্ষণ, যে রকম ক্যামোফ্লাজ করে থাকে জীবনের পাশাপাশি অদ্ভুত মরণ।
ত্যাগ বিরহ যন্ত্রণা কষ্ট সন্ন্যাস কবি হেলাল হাফিজের একধরনের সম্পদ কিন্তু ঘনিষ্ঠ আর একজন কবিকে জানি ভোগ যাঁর কাছে প্রধান, জীবন যাঁর কাছে নিছক খেলা ছাড়া কিছু নয়। জীবন রঙ্গমঞ্চের মত, তিনি সেই মঞ্চে প্রতিনিয়ত অভিনয় করে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে আমার বুঝতে কষ্ট হয় কোন কথাটি বা কোন ব্যবহারটি তাঁর সত্যি এবং কোনটি মিথ্যে, কোনটি অভিনয়। সরল মনে তাঁর সবটুকুকেই সত্যি বলে মনে হয়। মনে হয় বলেই সম্ভবত আমাকে তিনি খুব পছন্দ করেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যসের নাম খেলারাম খেলে যা। বড় দক্ষ তুলিতে এঁকেছেন খেলারাম বাবর আলীকে। লুইচ্চউ! বদমাইশ বলে যে বাবর আলীকে সকলে গাল দেয় সেই বাবর আলীর চরিত্রটি যে সৈয়দ শামসুল হকের ভেতরের চরিত্র, তা অনেকটা পথ তাঁর সঙ্গে না চললে আমার সম্ভবত অনুমান করা হত না।
রুদ্রর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আমার ভগ্ন হৃদয়ের শুশ্রুষা করার দায়িত্ব সৈয়দ শামসুল হক নিজে থেকেই নিয়েছিলেন। তিনিই একদিন আমাকে নিয়ে চলেন রাঙামাটি। রাঙামাটি কখনও যাইনি আমি আগে। বিশাল বিশাল পাহাড় আর পাহাড়ের পায়ের কাছে জলের পুকুর, সে পুকুরের ধারে ঘাসে বসে সৈয়দ হক তাঁর নিজেরও মাঝে মাঝে যে একা লাগে বলেন। বলার সময় এত চমৎকার চমৎকার শব্দ তিনি ব্যবহার করেন যে মুগ্ধ হই। আমার শব্দগুলো তুলনায় তুলোর মত, যে কোনও ঘাসপোকাও য়চ্ছন্দে অনুবাদ করে দেবে, বাক্যগুলো এত নরম যে প্রায়ই আমার মুখের কাছে তাঁকে কান এগিয়ে আনতে হয়। রাঙামাটির মধ্যিখানে রঙিন একটি হোটেলে ঢুকে আমার কানের কাছেই তাঁর মুখ এগিয়ে এনে বললেন, একটি ঘর নিলেই তো চলে, তাই না?
আমি যদি বলি, না চলে না, তবে মনে হতে পারে যে আমি তাঁকে কোনও কারণে বিশ্বাস করছি না, তাঁকে দৃশ্চরিত্র বলে সন্দেহ করছি, কিন্তু সন্দেহের প্রশ্ন ওঠার যেহেতু প্রশ্ন ওঠে না, আমার যে তাঁকে নিয়ে মোটেও আশঙ্কা করার কিছু নেই, তা প্রমাণ করতে চেয়ে অত্যন্ত নিস্পৃহ নির্লিপ্ত কণ্ঠে কেমন আছর উত্তরে ভাল আছি বলার মত করে বলি, হ্যাঁ চলে।
তোমার অসুবিধে হলে বল, তাহলে দুজনের জন্য দুটি ঘর নিই।
আমার সরল উত্তর, আমার কেন অসুবিধে হবে? আমার কোনও রকম অসুবিধে নেই।
‘ঠিক বলছ তো?’
আমি উদ্বেগের ঘাড় চেপে প্রশান্ত মুখে অতি নিস্পাপ-অতি নিস্কলুষ সম্পর্কটির ধারে কাছে কোনও ক্লেদ উড়ে আসার আশঙ্কা অবান্তর বলে, হেসে, ‘নিশ্চয়ই’ বলি।
সৈযদ হক আমার পিঠে আলতো করে হাত রেখে বলেন, ‘তোমার একটি জিনিস আমার বেশ ভাল লাগে, তুমি না বল না কিছুতে।’
তা ঠিক। আমি না বলি না কিছুতে। সৈযদ হক, আমার বাবার বয়সী লোকটি, যাকে আমি বাবা বা দাদা বলে ভাবতে পারি অনায়াসে, অথবা কোনওরকম আত্মীয-সম্পর্কের তুলনা না করলে বন্ধুই ভাবতে পারি— তাঁকে না বলব কেন! আমি না বলব কেন, আমি তো তাবৎ অকবির মত ঘরকুনো রক্ষণশীল নই, সংসারবৃত্তে খাবি খাওয়া, সংকুচিত, সংকীর্ণ মনের কেউ নই! এর আগে আমাকে আর ইয়াসমিনকে নিয়ে সৈয়দ হক গিয়েছিলেন কুমিল্লার শালবন বিহারে, ওখানেও বন উন্নয়ন দপ্তরের একটি অতিথি ভবনে ছিলাম আমরা। আমি আর ইয়াসমিন ঘুমিয়েছিলাম এক ঘরে, তিনি আরেক ঘরে। সকালে বন উন্নয়নের নাস্তার ঘরে গিয়ে নাস্তা খেয়ে শালবন বিহারে হেঁটে বেরিয়ে ঢাকা ফিরে এসেছি। সারা পথই সৈয়দ হক মূলত একাই কথা বলেন, নিজের শৈশব কৈশোরের কথা, দারিদ্রের কথা, নিজের যক্ষা রোগের কথা, যক্ষা রোগীকে হাসপাতালে যে ডাক্তারটি ভাল করে তুলেছিলেন, সেই ডাক্তার আনোয়ারার কথা, তাঁদের প্রেমের কথা, কী করে তাঁদের বিয়ে হল সেই কথা, দুটি ছেলে মেয়ের কথা, নিজের লেখালেখির কথা, আশেপাশের মানুষের নির্লজ্জ আর নিষ্করুণ চরিত্রের কথা নির্দ্বিধায় বলে যান। লেখালেখির প্রসঙ্গ এলে বড় আগ্রহ নিয়ে আমি কী লিখছি জানতে চান। বড় অপ্রতিভ বোধ করি তখন। শরমে মিইয়ে যাই। মাঝে মাঝে শখের কবিতা লিখি, আমার কবিতা সৈয়দ হকের মত বিশাল মানুষের কাছে উপস্থিত করার মত দুঃসাহস আমি করি না। বরং বিভোর হয়ে তাঁর ধীরতা, উদারতা, তাঁর মহানুভবতা, তাঁর মমত্ব দেখি। তিনি বিলেতে থাকা লোক, ঢাকার গুলশানে বাড়ি গাড়ি নিয়ে সচ্ছঅল জীবন যাপন করেন। দেশের নামকরা লেখক। দেশময় ঘুরে বেড়ান। অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর। এত জানেন, তবু জানার ইচ্ছে আরও। আরও তিনি দেখতে চান, খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁটে খুঁটে। জীবনের স্বাদ সাধ তাঁর কখনও ফুরোয় না। আমাদের মত মফস্বলের দুটি মেয়েকে তিনি খাতির করছেন, তাঁর খাতির পেয়ে আমরা দুবোন উচ্ছসিত, কিছুটা কুণ্ঠিত। তাঁর একটি ব্যপার লক্ষ্য করে অবাক না হয়ে পারি না, এত তিনি উন্মুক্ত, এত তাঁর ব্যাপ্তি, ময়মনসিংহে আমাদের বাড়িতে তিনি আতিথ্য বরণ করেছেন, অভাবনীয় সমাদর পেয়েছেন কিন্তু ঢাকায় নিজের বাড়িতে তিনি কখনও আমাদের একবার যেতেও বলেন না, রাত কাটাতে বলা তো দূরের কথা। রাত বরং তিনি দূরে কোথাও কাটাতে ভালবাসেন। দূরে কোথাওএর শখ আমারও কম নয়, দেশটির কত কোথাও এখনও যাইনি, কত কি দেখার বাকি। ছোট্ট একটি দেশ, তার বেশির ভাগ অঞ্চলই না দেখা পড়ে আছে। এদিকে বিচ্ছিরিরকম বয়স বাড়ছে।
রাঙামাটির রাঙা-রূপ দেখে একজনের কথাই আমার বার বার মনে পড়েছে, সে চন্দনা। চন্দনা নিশ্চয়ই এই মাঠটিতে হেটেঁছে, এই পুকুরের পাশে নিশ্চয়ই ও বসেছে, ওই গাছতলায় নিশ্চয়ই ও শৈশব জুড়ে দৌড়েছে, খেলেছে, কী খেলা খেলত চন্দনা! কোনওদিন ও গোল্লাছুট খেলেছে কি? না খেলে থাকলেও ওর জীবনেই ও খেলেছে খেলাটি, গোল্লা থেকে ছুটে গেছে চন্দনা। রাঙামাটির চাকমা জীবনের গোল্লা থেকে বাঙালি জীবনে ছুটে গেছে। চন্দনা কি সুখে আছে! বড় জানতে ইচ্ছে করে। মনে হয় হাজার বছর পার হয়ে গেছে ওকে দেখি না। শেষ দেখা হয়েছিল রুদ্রর মুহম্মদপুরের ভাঙা বাড়িটিতে। ওখানে ও খোকনকে নিয়ে এসেছিল, ওকে আপ্যায়ন করার ক্ষমতাও আমার ছিল না, বাইরে যে দুপুরে একসঙ্গে খেতে যাব, সেও হয়নি। এর আগে অবশ্য ঢাকায় ওর স্বামীর বোনের বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম, বাড়িতে চন্দনা কেমন জবুথবু বসে থাকত, ছোট একটি ঘর ছিল যেখানে ও আর খোকন ঘুমোতো, আমার বিশ্বাস হয়নি চন্দনা কোনও পুরুষের সঙ্গে ঘুমোয় এখন, কোনও পুরুষকে খাবার চিবোতে দেখলে,খালি গায়ে দেখলে চন্দনার বমির উদ্রেক হত, সেই চন্দনা। সেই উচ্ছল উদ্দাম চন্দনা, জীবন নিয়ে গোল্লাছুট খেলা চন্দনা, চাকমা সমাজে শ্রাদ্ধ হওয়া চন্দনা। এখন সত্যিই কি ও নিপূণ সংসারী! আমার বিশ্বাস হতে চায় না। কেবল মনে হতে থাকে, চন্দনা যেখানেই যার আলিঙ্গনেই আছে, ভাল নেই। চন্দনা কি এখন আগের মত কবিতা লেখে আর!
রাঙামাটি থেকে কাপ্তাই যাওয়ার পরিকল্পনা করেন সৈয়দ হক। কাপ্তাইএ তাঁর ভক্ত বৃন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে, ওখানে ওদেরই অতিথি হবেন তিনি। কাপ্তাই পৌঁছে যে কাজটি করলেন, আমি তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি তাঁর ভক্তবৃন্দকে আমার পরিচয় দিলেন, তাঁর কন্যা। তাঁর কন্যাকে ভক্তবৃন্দ দেখেনি কখনও, সুতরাং কন্যা আমি তাঁর হতেই পারি। লেকের জলে বড় একটি নৌকোয় বসে সৈয়দ হক ভক্তবৃন্দের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন হাসিমুখে। নতুন কি বই লিখলেন, কবিতা লিখছেন নাকি উপন্যাস, নাকি কাব্যনাট্য, নাকি গল্প। আমার পাশে একজন ভক্ত ছিল বসা, যেহেতু সৈয়দ হকের কন্যার সঙ্গে বাক্যবিনিময় না করা অভদ্রতার লক্ষণ, লাজুক হেসে বলল, ‘কাপ্তাই এ প্রথম এসেছেন?’
‘হ্যাঁ প্রথম।’
‘আপনাদের বাড়ি তো ঢাকার গুলশানে, তাই না?’
বুকের ধুকপুক নিজের কানে শুনি, আমি জলের দিকে চোখ ফেরাই, যেন ভক্তের বাক্যটি আমি ঠিক ষ্পষ্ট শুনিনি।
এরপর আবার প্রশ্ন, ‘আপনার বাবার লেখা সব আপনি পড়েছেন নিশ্চয়ই।’
এবার তাকাই, ‘কি বলছেন?’
‘বলছিলাম, হক ভাইএর সব লেখা নিশ্চয় পড়েছেন?’
‘ও। সব না, কিছু পড়েছি।’
বলে আমি আবার জলের দিকে, চাইছিলাম মন দিয়ে আমার জল দেখা দেখে ভক্তটি ভাবুক আমি জল নিয়ে বড় বেশি মগ্ন, এ সময় প্রশ্নবাণে বিরক্ত হতে চাই না। কিন্তু সেই ভক্ত তো আছেই, আরও একটি ভক্ত যোগ দেয় আমাকে সঙ্গ দিতে।
নতুন ভক্তটির প্রশ্ন, ‘আপনি কি শিগরি লন্ডন ফিরে যাচ্ছেন?’
জল থেকে চোখ তুলিনা আমি, ভয়ে আমার অনন্তরাত্মা কাঁপে। কী উত্তর দেব আমি এই প্রশ্নের আমি জানি না। যেন কারও কোনও প্রশ্ন শুনিনি আমি, আমি কানে খাটো, সৈয়দ হক বড় লেখক হতে পারেন, তাঁর নাকে কানে গলায় কোনও অসুবিধে না থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর কন্যার যে থাকবে না তার কোনও যুক্তি নেই। মনে হতে থাকে, এই নৌকো থেকে যদি জলে ঝাঁপ দিতে পারতাম, তবে কোনওরকম প্রশ্নের সামনে আমাকে পড়তে হত না।
‘আপনার মেয়ের নাম কি হক ভাই?’ কেউ একজন জিজ্ঞেস করল।
সৈয়দ হক মধুর হেসে বললেন, ‘ওর নাম অদ্বিতীয়া।’
‘বাহ, বেশ সুন্দর নাম তো।’ সেই একজন বলল।
‘নামটি রেখেছি আমি।’
সৈয়দ হক বেশ স্নেহচোখে তাঁর অদ্বিতীয়াকে দেখছেন। অদ্বিতীয়ার করুণ চোখদুটো দেখছেন। চোখে জল জমতে চাইছে দেখছেন। দেখেও মধুর হাসিটি তিনি ঝুলিয়ে রেখেছেন ঠোঁটে। ঝুলে থাকা হাসির তল থেকে বললেন, ‘অবশ্য ওর মা ওকে অন্য নামে ডাকে। .. কী, কথা বলছ না কেন অদ্বিতীয়া, তোমার ভাল লাগছে তো?’
আমি মাথা নেড়ে ভাল লাগছে জানিয়ে, যেহেতু ভাল না লাগাটা অশোভন এই চমৎকার নৌকো ভ্রমণে, চোখ ফেরালাম জলে।
জলের চোখ জলে।
সৈয়দ হক প্রায়ই তাঁর শার্ট খুলে গলা থেকে পেট অবদি কাটা হৃদপিণ্ডে অস্ত্রেপাচার করার দাগ দেখিয়ে বলেন তিনি বেশিদিন নেই। বেশিদিন তিনি নেই বলে আমার একধরণের মায়া হয় তাঁর জন্য। ওই মায়ার কারণেই কি না জানি না আমি চেঁচিয়ে বাবাকে ভাই বলে ডেকে উঠছি না, খুব সতর্ক থাকছি মুখ ফসকে যেন কোনও সম্বোধন বেরিয়ে না যায়। অভিনয়ে পাকা হলে নৌকোভরা দর্শক শ্রোতার সামনে হয়ত বলে বসতাম, বাবা তুমি কি দুপুরের ওষুধদুটো খেয়েছো?
সৈয়দ হক নাটক লেখেন, নাগরিক নাট্যগোষ্ঠীর জন্য বেশ কটি নাটক লিখেছেন। ইদানীং আবার শেক্সপিয়ারের নাটক অনুবাদ করছেন, কোন এক ইংরেজ নাট্যকার সেই নাটক পরিচালনা করছেন। সৈয়দ হক কেবল নাটক লেখেন না, জীবনেও নাটক করেন। নাটক না হলে এ কী! তিনি আমাকে কন্যার মতো বললেও না হয় পার পাওয়া যেত, একেবারে কন্যাই বলছেন। এই যে তিনি এত সম্মান পাচ্ছেন এখানে, একটুও ভয় করছেন না যদি আমি বলে ফেলি যে আমি তাঁর কন্যা নই! মিথ্যুক হিসেবে প্রমাণিত হলে কোথায় যাবে তাঁর সম্মান! ফেলি ফেলি করেও তাঁর সম্মান জলে ছুঁড়ে ফেলতে আমার স্পর্ধা হয় না, সম্মান তো সৈয়দ হককে আমিও কম করি না। কিন্তু আমাকে মঞ্চে তুলে দিয়ে তিনি কি মজা করছেন! তাঁর নিজের নামটি খোয়াতে হয়নি, তাঁর পরিচয়েই তিনি আছেন, কেবল আমাকে রেখেছেন ঢেকে। আমি না পারছি তাঁকে হক ভাই বলে ডাকতে, না পারছি আপনি বলে সম্বোধন করতে। জিভের ডগায় শব্দগুলো যখনই আসে, তখনই আমাকে গিলে ফেলতে হয়, শব্দগুলো জিভের জলের সঙে গিলতে গিলতে দেখি জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। নৌকো ভ্রমণ শেষ করে কাপ্তাই বাঁধ দেখে তিনি নৌবাহিনীর আগপাশতলা ঘুরে দেখলেন, আমি পেছন পেছন, বোবা কালা অদ্বিতীয়া। রাতে এক নৌসেনার বাড়ি নেমন্তন্ন, ওখানে বাড়ি ভরা লোকের সামনে ওই একই পরিচয় আমার, সৈয়দ হকের কন্যা। নাম অদ্বিতীয়া। নৌসেনা আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করাতে সৈয়দ হক হা হা করে ছুটে এলেন, ‘ওকে আপনি বলছেন কেন! তুমি করে বলুন। বয়স তে একুশও পেরোয়নি, এই তোর কি একুশ হয়েছে?’ পঁচিশ ছাড়িয়ে যাওয়া মেয়ে আমি মাথা নোয়াই। পায়ের আঙুল গুনি, দশটি জেনেও গুনি আবার। গোনা শেষ হলে মনে মনে গুনি হাতের আঙুল, হাত শেষ হলে আবার পায়ের। সৈয়দ হক মদ্যপান করছেন তখন। ‘আচ্ছ! আপনার মেয়ে খুব কম কথা বলে বুঝি?’
‘ঠিক বলেছেন। খুব কম কথা বলে। জানি না কোত্থেকে এত লজ্জা সংগ্রহ করেছে ও। কোত্থেকে রে? ময়মনসিংহ থেকে?’ সৈয়দ হক চোখ টিপলেন।
ময়মনসিংহের ওঁরা কিছুই জানেননা।
নৌসেনার স্ত্রী সেজে গুজে ছিলেন, তিনি ধন্য ধন্য হাসি হেসে সৈয়দ হকের সামনে দাঁড়ালেন, ছবি তুলবেন। এক এক করে বাড়ির লোকেরা ছবি তুলল, পাশের বাড়ি থেকেও সৈয়দ হককে দেখতে লোক এসেছিল, ওরাও তুলল। সৈয়দ হক আমাকে প্রতিবারই ডেকে বসালেন তাঁর পাশে।
‘আপনার মেয়েও কি লেখে নাকি?’ নৌসেনার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।
‘লেখে, ও কবিতা লেখে। খুব ভাল কবিতা লেখে কিন্তু। তোমার লেখা একটি কবিতা শোনাও তো অদ্বিতীয়া।’
আমি সবেগে মাথা নাড়ি।
‘ভারি দুষ্টু ও। ভারি দুষ্টু।’ সৈযদ হক আমার ঘাড়ে চাপড় দিয়ে বললেন।
নৌসেনার বাড়ির লোক, এমনকী পড়শিরাও বললেন, সৈয়দ হককে তাঁরা টেলিভিশনে দেখেছেন। বিশাল ভোজনউৎসবে বসেও ওই এক কথা, টেলিভিশনে কবে কে তাঁকে দেখেছেন। একজনই কেবল সদর্পে ঘোষণা করলেন, তিনি তাঁর একটি বই পড়েছেন, বইয়ের নাম ‘আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি’। নাম শুনে আমি চমকে উঠি, চমকে উঠি কারণ এটি শামসুর রাহমানের বই! লক্ষ্য করি তিনি প্রতিবাদ করছেন না, বলছেন না যে এটি তাঁর লেখা বই নয়। একবার শুধু আমার দিকে তাকিয়ে আগের মত চোখ টিপলেন। তিনি, দেখে আমার মনে হয়, সবকিছুতেই খুব মজা পাচ্ছেন। দিন খুব বেশি না থাকলে বুঝি এই হয়, প্রতিটি মুহূর্তে বাঁদর নাচিয়ে আনন্দ করতে হয়। আনন্দ খুব বেশিক্ষণ করা সম্ভব হয় না তাঁর, বারবারই তিনি স্নানঘরে দৌড়োন। খাওয়া শেষে আমি ও ঘর হয়ে আসতে গেলে দেখি স্নানঘর ভেসে যাচ্ছে বমিতে। বেসিনগুলোয় উপচে উঠছে যা তিনি খেয়েছিলেন। নির্যাস নিস্ক্রান্ত হওয়ার পথও বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু অসুস্থ হয়ে তিনি যে কাত হয়ে আছেন কোথাও, তা নয়, বরং একটি হাসি ঝুলিয়ে রেখেছেন ঠোঁটে, যে হাসিটির আমি কোনও অনুবাদ করতে পারিনি।
আমাদের জন্য কাপ্তাইএর নৌঅতিথিশালায়, খামোকা দুটো ঘর নিয়ে টাকা খরচা করার কোনও মানে নেই বলে, কন্যার সঙ্গে একঘরে শুতে পিতার কোনও সংকোচ নেই বলে, সৈয়দ হক একটি ঘরই নিয়েছেন। ঘরটি বড়, ঘরটির দুদিকে দুটি বিছানা, হলে কী হবে, আমার ভয় হয় ঘরটিতে ঢুকতে। সৈয়দ হক মদ খেয়ে পুরো মাতাল। মাতালের সঙ্গে এক ঘরে রাত্রিযাপন করার ঝুঁকি নিতে আমার সাহস হয় না। এর পেয়ে ঘরের বাইরে বারান্দায় কিংবা গাছের তলে চট বিছিয়ে শুতে দিলে স্বস্তি পেতাম। নিজেকে শেষ পর্যন্ত ঠেলে পাঠাই ঘরে, যেন সৈয়দ হক আদৌ মদ খাননি, আমি যে তাঁর কন্যা এ কথা মিথ্যে নয় আমি তাঁর কন্যাই এমন একটি বিশ্বাসের আবরণে নিজেকে ঢেকে নিজের মধ্যে স্বতস্ফূর্ত গতি সঞ্চার করে সোজা নিজের বিছানায় কাঁথার তলে আপাদমস্তক ঢুকিয়ে ফেলি। গরমে কেউ কাঁথায় গা ঢাকে না, কিন্তু আমার উপায় নেই, কাঁথাটিই কোনও অঘটনের হাত থেকে বর্ম হয়ে আমাকে বাঁচাবে বলে মনে হতে থাকে। কাঁথা আমি শক্ত করে চেপে ধরে রাখি কোনও দস্যু এসে যেন কেড়ে নিতে না পারে। বুকের দপদপ শব্দ শুনছি আর ভয় হচ্ছে এই বুঝি খেলারাম এলেন হাঁটি হাঁটি পা পা করে শরীফার বিছানার কাছে।
‘তুমি কি ঘুমিয়ে গেছ?’
আমি নিরুত্তর থাকি। নিরুত্তর, যেন ঘুমোচ্ছি, ঘুমোতে থাকা মানুষ কারও প্রশ্ন শুনতে পায় না। আমিও তাঁর কোনও প্রশ্ন শুনিনি। আমি স্থির হয়ে থাকি, মৃত কাঠ হয়ে পড়ে থাকি বিছানায়। আলগোছে অন্ধকারে কাঁথা সামান্য সরিয়ে, যেন ঘুমের মধ্যে হাত নড়ে কাঁথাকে সরিয়ে দিয়েছে সামান্য, দেখি তিনি ধীরে ধীরে হাঁটছেন ঘরে। কেন হাঁটছেন, কেন তিনি ঘুমোচ্ছেন না! কী চান তিনি, আমাকে ঢাকা থেকে এতদূর নিয়ে আসার নিশ্চয়ই তাঁর কোনও উদ্দেশ্য আছে। অতিথিশালায় অনেকগুলো ঘর খালি পড়ে থাকার পরও, নৌসেনা ভদ্রলোকটি দুজনের জন্য দুটো ঘরের ব্যবস্থা করতে চাওয়ার পরও তিনি আমাকে কন্যা বানিয়ে একঘরে ঢুকিয়েছেন কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই, আমার বিশ্বাস হয় না। সারারাত বুকের ধুকপুকুনি শুনি, সারারাত ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি আর সারারাত তাঁর জেগে থাকার, তাঁর হাঁটার, তাঁর বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গে কথা বলার শব্দ শুনে যাই। মফস্বলি মেয়ে ঢাকার বড় লেখকের আচার ব্যবহারের কোনটি আসল কোনটি নকল কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।
সকালে সোজা বিমান বন্দর, সোজা ঢাকা, তিনি গুলশানের কাছে নেমে গেলেন, আমি বেবি ট্যাক্সি নিয়ে নয়াপল্টন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। মঞ্চ থেকে আনাড়ি অভিনেষনী নেমে এলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে না তো কী! তিনি বাড়ি অবদি বেবি ট্যাক্সি নিলেন না, স্ত্রী বা চেনা কেউ যদি আমার সঙ্গে তাঁকে দেখে ফেলে, তবে তাঁর বিপদ হবে বলে! মেয়েমানুষের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করে এসেছেন, এরকম কথা হবে বলে! তিনি সম্ভবত কথা এড়িয়ে চলতে চান, তাই আড়ালে আবডালে সারতে চান এরকম দুচারটে অভিসার। সম্ভবত আমাকে দিয়ে যা আশা করেছিলেন তা হয়নি বলে তিনি ক্ষুব্ধ, নিজের ওপর নিশ্চয়ই তাঁর রাগ হচ্ছে, এতগুলো টাকা বেহুদা খরচ হওয়ায় তাঁর আক্ষেপ হচ্ছে। খেলারাম খেলে যা উপন্যাসে বাবর আলী তাঁর অল্প বয়স্ক প্রেমিকাকে সহজে পেতে চায়নি, নানা কৌশল করে, দেশের এক কোণ থেকে আরেক কোণে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে তবেই কাজ সেরেছে। সৈয়দ হকের ভেতরে কোথাও কি তাঁর নিজেরই গড়া চরিত্র বাবর আলী বাস করে গোপনে! আমার এই প্রথম মনে হয়, করে। ফেরার পথে সারাক্ষণই তিনি চুপচাপ বসে ছিলেন, তাঁকে দেখতে লাগছিল অল্প চেনা কোনও লোকের মত, যেন আমার কেবল মুখ চেনেন তিনি অথবা নাম শুনেছেন, এর বেশি কিছু নয়। জানি না এ তাঁর আমাকে সঙ্গে নিয়ে কাজের কাজ কিছু না হওয়ায় মনোকষ্টের কারণে কী না। অথবা তিনি আনমনে তাঁর লেখার কথা ভাবছেন। অথবা বিমানে লোকদের তিনি খুব একটা জানতে দিতে চাননা যে তিনি তাঁর অর্ধেক বয়সী একজন অনাত্মীয়ার সঙ্গে ভ্রমণ করছেন। আমার অবয়বে আমি জানি লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না আমি যে তাঁকে একশ ভাগ বিশ্বাস করছি না তার, আমি তাঁর উদ্দেশ্য বিধেয় নিয়ে সামান্য হলেও সংশয় প্রকাশ করছি। না বোঝার ভান করা আমার স্বভাবের অন্তর্গত, বিশেষ করে কোনও অস্বস্তিকর সময়ে। আমাদের পুরুষেরা যখন বেশি বোঝার ভান করেন, তখন মেয়েদের না বোঝার ভান না করলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা থাকে। মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ থাকার কারণেই আশঙ্কা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আমি মেয়েদের এই কারণে বলছি, যে, পরে আমি ইয়াসমিনের কাছ থেকে একই রকম উত্তর শুনেছিলাম, সেও প্রচুর অশ্লীলতার আহবানকে যেন বোঝেনি কিছু বলে এড়িয়ে গেছে।
সৈয়দ হক হয়ত কোনও কুমতলব নিয়ে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাননি, বেড়াতে যাওয়ার জন্যই বেড়াতে যাওয়া কিন্তু আমাকে কন্যা হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যপারটি আমার মোটেও পছন্দ হয়নি। তাঁর কোনও প্রয়োজন ছিল না আমার পরিচয়টি লুকোনোর। আমি তাঁর মত বড় কবি বা লেখক নই, কিন্তু আমার তো একটি পরিচয় আছে। আমি কবি না হলেও কবিতা লিখি। লুকোছাপা তবে কী কারণে! তাঁর সঙ্গে আমার, সমাজ যা বৈধ বলে মানেনা সেই পরকীয়া প্রেমও চলছে না বা যৌনসম্পর্কও নেই।
সৈয়দ হক যখন ময়মনসিংহে গিয়েছিলেন, শামসুর রাহমানকে ফোন করে খামোকা কথা বলেছেন, শামসুর রাহমান কেমন আছেন, কি করছেন জানতে চাওয়ার পরই তিনি বলেছেন তিনি এখন ঢাকার বাইরে, ঢাকার বাইরে কোথায় শামসুর রাহমানকে তিনি অনুমান করতে বলেছেন, অনুমান সম্ভব না হলে তিনি বলেছেন খুব নয়, মাত্র একশ কুড়ি মাইল-মত দূরে এবং এখানে তিনি সুন্দরী রমণী দ্বারা বেষ্টিত। খবরটুকু জানিয়ে তিনি হেসে আমাকে বলেছেন, ‘শুনেছো তো, আমি কিন্তু বলিনি আমি ঠিক কোথায় কার আতিথেয়তা ভোগ করছি।’ আমার ঠিক বোধগম্য হয়নি, কেন এ বিষয়টি লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন তাঁর।
‘আপনি বললেই তো পারতেন আপনি আমার বাড়িতে আছেন।’
‘বলছ কী, সারা ঢাকা রাষ্ট্র হয়ে যাবে তো!’
‘রাষ্ট্র হলে অসুবিধে কী!’
সৈয়দ হক অদ্ভুত করে হেসেছিলেন। জানি না কি অসুবিধে সৈয়দ হকের। তবে তিনি কোন কোন রমণীর সঙ্গে শামসুর রাহমানের প্রেম হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যখন বর্ণনা করেন তাঁর চোয়ালে একটি ভাঁজ পড়ে, ভাঁজটি দেখে আমার মনে হয়েছে এ ঈর্ষা। ঈর্ষা তাঁকে মুঠোর ভেতর নিয়ে খেলছে। তাঁরও ইচ্ছে করে শামসুর রাহমানের মত বড় কবি হতে, তাঁরও ইচ্ছে করে রূপসী রমণীদের থরথর আবেগের স্পর্শ পেতে। ঈর্ষা শব্দটিও তাঁর প্রিয়, বন্যায় ভেসে যাওয়া ব্রহ্মপুত্রে বেড়াতে বেড়াতে তিনি জলমগ্ন চরাচরে একটি ছোট্ট গাছ দেখিয়ে বলেছিলেন, ‘ওই গাছটির নাম কি জানো? ওর নাম ঈর্ষা।’ ঈর্ষার মুঠো থেকে বেরিয়ে অথবা ওই মুঠোর ভেতরে নিজে যখন হাঁসফাঁস করেন, তখন তিনি নিজের প্রেমের কথা বলেন, তাঁর নিজের শ্যালিকা যেটি তাঁর বাড়িতে থেকে মানুষ হয়েছে, তার সঙ্গে গভীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাঁর, কেবল প্রেমই নয়, যতদূর প্রসারিত হতে পারে ঘনিষ্ঠতা, সবই। তার সেই শ্যালিকা পরে অল্প বয়স্ক এক যাচ্ছেত!ই ছেলের সঙ্গে প্রেম করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, এর চেয়ে বড় দুঃসংবাদ তাঁর জীবনে আর নেই, তিনি সইতে পারেন না শ্যালিকার এই না-থাকা। নিজে তিনি শ্যালিকার বাড়ি গিয়ে টাকা পয়সা দেন নিয়মিত, তার নতুন সংসারে যা প্রয়োজন সবই তিনি কিনে দিয়েছেন। সৈয়দ হক অনর্গল বলে যান শ্যালিকা কি করে এই বিয়েটি করে তাঁকে চরম অপমান করেছে, হৃদয়ে যা কিছু ছিল সব ছিনিয়ে তাঁকে শূন্য করে দিয়েছে। আমি জানিনা কেন তিনি আমার কাছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সব খুঁটিনাটি খুলে বলেছেন। মাঝে মাঝে তাঁকে মনে হয়েছে বড় নিঃসঙ্গ মানুষ তিনি। তাঁর হয়ত কেউ নেই যার কাছে তিনি তাঁর সুখের কথা, তাঁর কষ্টের কথা বলতে পারেন। মায়া হয়েছে তাঁর জন্য। আবার মনে হয়েছে গল্প লেখকদের বোধহয় এমনই স্বভাব, গল্প লেখেন যেমন, বলেনও তেমন। সত্য ঘটনার সঙ্গে এর যে কোনও সম্পর্ক থাকবে তার কোনও কথা নেই। তিনি একদিন বলেছেনও, যখন তিনি ছোট, ঘুর পথে বাড়ির দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে তিনি সবাইকে জানিয়েছেন, বড় দরজার পাশে বিশাল এক কুকুর দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ে তিনি বড় দরজা মাড়ান নি। তিনি মিথ্যে বলেছেন, কোনও কুকুর বড় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল না, কিন্তু বলেছেন যে দাঁড়িয়ে আছে, বলার কোনও কারণ নেই, কাউকে ভয় দেখানোর জন্য নয়, এমনি বলা।
‘এমনি বলা?’
‘হ্যাঁ এমনি বলা।’
লেখক হওয়ার সম্ভাবনা সম্ভবত ওই কুকুরের গল্পটি দিয়েই শুরু হয়েছিল। সৈয়দ হক এরকম প্রায়ই মিথ্যে বলেছেন, কোনও কারণ নেই তারপরও বলেছেন। জীবনকে তিনি একটি ছোটগল্পই মনে করেন হয়ত। তবে তিনি যা খুশি তাই মনে করে যে কথাই বলুন বা যে গল্পই করুন না কেন, চমৎকার কথা তিনি বলেন, অসামান্য গল্প তিনি করেন, আমি তা অস্বীকার করি না। তাঁর এই একটি গুণ আমাকে সবসময়ই মুগ্ধ করেছে।
অবকাশের অসাধারণ খাতির যত্ন সৈয়দ হকের একবারই জুটেছে। যখন সকাল কবিতা পরিষদের অনুষ্ঠানে এলেন ময়মনসিংহে, তখন। অবকাশেই তাঁর থাকার আয়োজন করেছিলাম। বাবার কি হবে মনের অবস্থা, চিৎকার করে বাড়ি ফাটাবেন কী না, সৈয়দ হককে আঙুল উঁচিয়ে কালো ফটক দেখিয়ে দেবেন কী না, কিছুই না জেনে তাঁর থাকার আয়োজন বাড়িতে। ভীষণ ঝুঁকি নেওয়া বটে। মাকে লেলিয়ে দিলাম বাবাকে বোঝাতে দেশের সবচেয়ে বড় লেখক, বড় বুদ্ধিজীবী এই সৈয়দ শামসুল হক, তাঁর সঙ্গে যেন জানোয়ারি না করেন। দাদাকেও লেলিয়ে সৈয়দ হকের যত রকম প্রশংসা করা যায় করিয়ে বাবাকে রাজি করিয়েছিলাম এ বাড়িতে সৈয়দ হককে দুদিনের জন্য অতিথি করার অনুমতি দিতে। বাবা দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেল বাড়িতে। বাজারে মেলে হেন ভাল জিনিস নেই যে কেনা হল না। রান্নাঘরে ধুম পড়ে গেলে রান্নার। আমার ঘরটি ধুয়ে মুছে সাজিয়ে গুজিয়ে দেওয়া হল সম্মানীয় অতিথিকে। বাবা জানোয়ারি করা তো দূরের কথা, রীতিমত সৈয়দ হকের সঙ্গে স্যুট টাই পরে খেতে বসেছেন, বাড়িতে এসে চিৎকার চেঁচামেচি করার অভ্যেসকে মাচায় তুলে রেখে দুদিন তিনি মানুষের মত আচরণ করেছেন।
দ্বিতীয়বার অবকাশে তাঁর আর থাকা হয়নি, কারণ হচ্ছে ছোটদা। সৈয়দ হকের পদধূলি অবকাশে পড়ার পর যে ধন্য ধন্য ভাব ছিল বাড়ির সবার মধ্যে, একদিন ছোটদা সেই ধন্যভাবের দুধে পাঁচ ফোটা চোনা ছিটিয়ে দিলেন। বলে গেলেন ‘সারা ঢাকা শহর জানে হকুর কীর্তিকলাপ, মেয়েমানুষ লইয়া ফুর্তি করার ওস্তাদ এই হকু। লুইচ্চা।’ ব্যস, সৈয়দ হক নিষিদ্ধ অবকাশে, নিষিদ্ধ বলে তিনি যে ময়মনসিংহে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তা নয়, এসেছেন, সার্কিস হাউজের অতিথিভবনে থেকেছেন। তিনি, সারা দেশই, বলেছেন, ঘুরে বেড়ান। ঘুরে বেড়ালে অভিজ্ঞতা বাড়ে। মানুষ দেখতে হয়, মানুষ। মানুষের চেয়ে চমৎকার কিছু আর জগতে নেই। মানুষ কী করে কথা বলে, কী করে হাসে, কী করে লজ্জা পায়, কী করে ভয় — সবই হচ্ছে দেখার বিষয়। সৈয়দ হকের প্রায় পদতলে বসে আমি হাঁ হয়ে শুনে গেছি তাঁর দর্শন। ঢাকায় নয়াপল্টনে ছোটদার বাড়িতেও তিনি এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, ছোটদা সামান্য সৌজন্যও দেখাননি। ছোটদার ওপর রাগও হয়েছিল আমার বিষম। সারা ঢাকা শহর জানে বলে তিনি যে মন্তব্যটি করেছেন, তা তাঁর নিজের নয়, অন্য একজনের, যে অন্যটি বিমানের কোনও কর্মচারি অথবা কোনও ভুতপূর্ব চিত্রালী-লেখক। সারা ঢাকা শহর জানে এই কথার পেছনে কোনও যুক্তি নেই। ঢাকা শহরের বেশির ভাগ লোক, সাহিত্য জগতে যাদের পদচারণা নেই, সৈয়দ হককে চেনেই না, সাহিত্যজগতে যাদের আছে, তাদের বেশির ভাগই সৈয়দ হককে শ্রদ্ধা করেন। যাই হোক, দুধচোনাটিকে বিশুদ্ধ দুধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবকাশে সৈয়দ হক নিষিদ্ধ হয়েই রইলেন, নিষিদ্ধ হয়েছিলেন বলে তাঁর প্রতি পক্ষপাত আমার বেশি ছিল। তিনি ডাকলেই আমি দেখা করতে গিয়েছি, সে সার্কিট হাউজে হোক, রেস্তোরাঁয় হোক, ঘুরে বেড়াতে মুক্তাগাছা হোক। কুদ্দুস বয়াতির ওপর তথ্যচিত্র বানাতে যখন তিনি নদীর পাড়ে ব্যস্ত, সেখানেও তাঁর ডাক পেয়ে ছুটে গিয়েছি।
সৈয়দ হকের সঙ্গে আমার সম্পর্কটি স্নেহ শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। একজন বড় লেখকের, মাঝে মাঝে কবিতা টবিতা লেখার অভ্যেস আছে এমন সাহিত্য অনুরাগী ছেলে মেয়েদের প্রতি যে সহমর্মিতা থাকে, আমার প্রতি তা-ই ছিল তাঁর। সেটি ক্রমে ক্রমে বাক্তিগত হয়ে উঠল, বিশেষ করে তিনি যখন রুদ্রর সঙ্গে কেন আমি বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইছি তার কারণটি জানতে চেয়েছিলেন এবং সে কারণে ময়মনসিংহ অবদি এসেছিলেন। সাহিত্যিক বা অসাহিত্যিক যে কথাই হত তাঁর এবং আমার মধ্যে, মূল বক্তা ছিলেন তিনিই। তাঁকেই বক্তা হিসেবে মানায়। ইয়াসমিনকেও তিনি ‘এই কি করছিস কেমন আছিস, কাছে আয় তো, বোস এখানে’ বলে লজ্জায় লাল হয়ে থাকা ইয়াসমিনকে কাছে বসিয়ে রাজ্যির গল্প শোনাতেন। উপদেশও দিতেন। উপদেশ আমাকেও দিতেন, কি করে কবিতা লিখতে হয়, কি করে ছন্দের জন্য শব্দ না গুনে কানকে সজাগ রাখতে হয় বলতেন। মন দিয়ে আমার সব কবিতাই তিনি পড়েছেন, প্রায় প্রতিটি কবিতা নিয়ে কিছু না কিছু বলেছেন, কোনটি ভাল হয়েছে, কোনটি কী হলে ভাল হত, কোন শব্দটি না বসিয়ে কোন শব্দটি বসালে বেশ শোনাতো — এসবে তাঁর কোনওরকম কৃত্রিমতা ছিল না। ইয়াসমিনের হঠাৎ অবকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে আমি যেমন ভেঙে পড়েছিলাম, সৈয়দ হকও তেমন। সৈয়দ হক আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে কাঁদলেন হাউ মাউ করে, কাঁদলেন ইয়াসমিনের জন্য। পরে ইয়াসমিনের নতুন বাড়িতে তিনি বেশ কবার গেছেন নেমন্তন্ন খেতে। একবার, আমি তখন ঢাকায়, তিনি তাঁর অল্প বয়সী এক প্রেমিকাকে নিয়ে ইয়াসমিনকে দেখতে গেলেন। সারাদিন ইয়াসমিনের ঘরে মেয়েটির সঙ্গে খুনসুঁটিতে মেতে ছিলেন। জড়িয়ে ধরা, চুমু টুমু সবই চলেছে। নতুন বাড়িতে ইয়াসমিনের অস্বস্তির শেষ নেই, ওর বয়স্ক অতিথি একটি বাচ্চা মেয়ে নিয়ে খালি ঘরে কী করছে বাড়ির অনেকে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছিল ওর দিকে। এই মেয়েটিকে আমি আর ইয়াসমিন দুজনই দেখেছিলাম সৈয়দ হকের অনুবাদে টেম্পেস্ট নাটক যেদিন হয়েছিল ব্রিটিশ কাউন্সিলে। আমরা তিনজন পাশাপাশি বসেছিলাম, পেছনের আসনে সৈয়দ হক। পেছন ফিরে ক’বার দেখেছি তাঁর চোখ নাটকে নয়, চোখ মেয়েটিতে। এই মেয়েটি পাঁচতলার ছাদ থেকে পড়ে আত্মহত্যা করতে নিয়েছিল এমনই গভীর ছিল তার ব্যক্তিগত শোক, সেই শোক থেকে তিনি তাকে উঠিয়ে এনে জীবনের এক দ্যূতিময় রূপ দেখিয়েছেন, মেয়েটির ভেতর সঞ্জীবিত করেছেন ভালবাসার বোধ — তিনি আমাকে বলেছেন সব।
কখনও সৈয়দ হক অবিকল বাবার মত, ভাল ভাল উপদেশ বর্ষণ করছেন, কখনও বড় ভাইয়ের মত আগলে আগলে রাখছেন, কখনও সমবয়সী বন্ধুর মত সরস কথাবার্তা বলছেন, কখনও আবার তাঁর দুটো চোখে হঠাৎ ঝলসে ওঠে নেকড়ের নীল হাসি। মাঝে মাঝে মনে হয় ঝলসে উঠছে, আবার কখনও মনে হয় না উঠছে না। রাঙামাটি আর কাপ্তাই এ এক ঘরে ঘুমোবার ইচ্ছে করার সময় তাঁর ভেতরের বাবর আলীটি জেগে উঠেছিল, আরেক বার মনে হয় না জেগে ওঠেনি। ঘনিষ্ঠতার শুরু থেকে সৈয়দ হক আমাকে দোদুল দোলায় দুলিয়েছেন। রুদ্রকে কেন আমি আমি ত্যাগ করতে চাই তা জেনে আমার বেদনার্ত মনে তাঁর সমবেদনা বুলোতে তিনি যখন আমার পিঠে হাত রেখেছিলেন ময়মনসিংহের এক রেস্তোরাঁয় খেতে বসে, ঠিক ব্রার হুকের ওপর হাতটি পড়েছিল তাঁর, পিঠ আমার ধনুকের মত বেঁকে গেছে মুহূর্তে, সরিয়ে দিতে চেয়েছি তাঁর ওই সমবেদনার কোমল হাতটি। মনে হয়েছিল খেলারাম বুঝি আমার সঙ্গে এত দূর অবদি এসেছেন খেলতে। সৈয়দ হকের জন্য আমার শ্রদ্ধা যেমন অগাধ, তাঁকে নিয়ে আমার সংশয়ও তেমন অপরিসীম। এই সৈয়দ হক আমাকে মুগ্ধ করেছেন সকাল কবিতা পরিষদের অনুষ্ঠান এবং আমার সাহিত্যকর্ম নিয়ে দৈনিক পত্রিকায় একটি চমৎকার কলাম লিখে। আবার এই সৈয়দ হকই তাঁর বাড়িতে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, খালি বাড়িটির আগপাশতলা দেখাতে গিয়ে তাঁর ছবি আঁকার ঘরটিতে নিয়ে ঘরটির বন্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন, যেন এই আমাকে আটকেছেন, এখন তাঁর আকাঙ্খার তুলিতে আমার সাদা শরীর রঙিন করবেন। মূহূর্তে আমার মাথা একটি ঠান্ডা ভয় ছড়িয়ে যায় সমস্ত শরীরে, তাঁকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত দরজা খুলে বেরিয়ে যাই। এই সৈয়দ হকই হদপিন্ডে অস্ত্রোপাচারের সামান্য আগে লন্ডনের হাসপাতাল থেকে, বলেছেন যে, প্রথম যে মানুষকে ফোন করেন দেশে, সে আমি। এই সৈয়দ হকই আমার কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে ঢাকায় তাঁর প্রকাশককে চিঠি লিখে দিয়েছেন যেন আমার বই ছাপে। এই সৈয়দ হকই খবরের কাগজে আমাকে দিয়ে কলাম লেখানোর জন্য নাইমকে পরামর্শ দিয়েছেন। এই দেবতার মত মানুষটিকে তারপরও সবসময় দেবতার মত বলে মনে হয়নি আমার। কিন্তু সে কেবল মনে না হওয়ার ব্যপার, তাঁর কোনও অশ্লীলতা,ভাল, যে, আমার কখনও দেখতে হয়নি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এ আমার অহেতুক সংশয়, এ আমার অমূলক ভয়, জগত না দেখা জীবন না চেনা ভীরু কিশোরীর মত যেখানেই পা দিই ভাবি বুঝি ফাঁদ পাতা, এ তাঁকে বোঝার ভুল, আসলে সৈয়দ হক যেমন উদার, তেমন উদারই, যেমন বড় তিনি, তেমন বড়ই। অথচ এই সৈয়দ হকই তাঁর কলামগুলো যখন বই হয়ে বেরোয়, ময়মনসিংহে তসলিমা নাসরিনের সাহিত্যানুরাগ এবং তার সকাল কবিতা পরিষদ নিয়ে যে প্রশংসা টুকু ছিল, আলতো করে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। সে পরের দিকের ঘটনা, আগে উনআশির প্রথম দিকের কথা বলি।
উনাশিতে অনেক মন্দ কিছু ঘটেছে, মন্দের মধ্যে আমাকে নিঃস্ব করে ইয়াসমিনের চলে যাওয়াটিই সবচেয়ে মর্মান্তিক। তখন আমি বিষণ্নতার গভীরে আকণ্ঠ ডুবে আছি। চেনা চারপাশ থেকে অচেনা কোথাও যেতে চাই। আমার এত প্রিয় শহর ময়মনসিংহ, অথচ মনে হতে থাকে যেন এ শহরটি আমার জন্ম জন্মান্তরের শত্রু। এত খাঁ খাঁ অন্য কোনও শহর করে না। অবকাশে ইয়াসমিনের হারমোনিয়ামটির ওপর ধুলো জমতে থাকে। হারমোনিয়ামের ওপর গীতবিতানটি পড়ে থাকে অসহায়। আমার সয় না। সয় না ওর জামা কাপড়, ওর শখের এটা সেটা, ওর কবিতার বইগুলোর উদাস পড়ে থাকা। শহর থেকে পালাই আমি। শীতলক্ষার তীরে উদাস বসে থাকি আমি তখন, সঙ্গে ইমদাদুল হক মিলন। গল্প উপন্যাস লিখে জনপ্রিয় হওয়া মিলন প্রেম-প্রেম চোখে তাকায় আমার দিকে। মিলনের সঙ্গে পরিচয় আমার আজকের নয়। সেই সেঁজুতি ছাপার সময় তার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি ছিল। সুন্দর সুন্দর রোমান্টিক চিঠি লিখত মিলন। প্রেমের জলে ডোবানো এক একটি থর থর শব্দ। মিলন আমাকেই নয় শুধু, যে কোনও মেয়েকেই ওরকম করে লিখত। একবার সে টাঙ্গাইলে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে মুক্তিকে দেখে, বিশেষ করে মুক্তি যখন আমার মুক্তি আলোয় আলোয় গানটি গাইল, প্রেমে পড়ে গেল। মুক্তি কবিতা লিখত। মিলন আর মুক্তির প্রেম দীর্ঘদিন ধরে দুজনের মিলন ঘটিয়ে দুজনকে একসময় মুক্তি দিয়ে দিল। মিলন, মুক্তি আর লিমা নামের একটি চরিত্র নিয়ে সন্ধানীর নিকষিত হেম এ কান্না পায় পায় এমন একটি বিরহের গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্পটি অনেকে পড়ে ভেবে নিয়েছিল লিমা চরিত্রটি আমিই। মনে মনে নিজেকেই কি আমি কল্পনা করিনি লিমা চরিত্রে! করেছি। মিলনের জন্য সেই কিশোরী বয়সে আমার একধরনের রিনিকি ঝিনিকি সাধ ছিল, রোমান্টিক কোনও যুবকের জন্য যেমন থাকে যে কোনও প্রেমোন্মুখ কিশোরীর। রুদ্রর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল মিলনের, রুদ্রর সঙ্গে পরে মুক্তির আরও ভাল বন্ধুত্ব হয়েছিল। রুদ্রর সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীন মিলনের সঙ্গে বইমেলায় আমার দেখা হত। দুচারটে মামুলী কথাবার্তা হত। সেই মিলন। সেই আমি। মিলন যেন তেন এক গোবেচারা মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করতে শুরু করেছে আর আমি সংসারের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসা ডানায় করে একাকী একটি জীবন নিয়ে ঠিকানাহীন ঘুরে বেড়ানো আহত ক্লান্ত পাখি। মিলন আমাকে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে এক জগত আছে, সেই জগতের কথা বলে। তখনই আমার ইচ্ছে হয় দূরে বহু দূরে কোথাও চলে যেতে। কতদূর গেলে খুব দূরে যাওয়া হয় আমি জানি না। এই ভূবনে স্বর্গ বলে একটি জায়গা আছে কোথাও, তাপে শাপে দগ্ধ প্রকৃতি থেকে চোখ সরিয়ে বলি, ‘চল কাশ্মীর চল।’ মিলন সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ‘চল।’
শীতলক্ষার শীতল জলে শীতল চোখ রেখে মিলন বলে, ‘শোন, তিরিশ পয়ত্রিশ হাজার টাকা কিন্তু লাগবে যেতে হলে।’
অত টাকা নেই আমার কাছে। মাস গেলে দু হাজার টাকা মাইনে পাই। জমানো যা ছিল তা বই বের করতে গেছে। টাকা ধার করে নিজেকে হারিয়ে যাওয়ার যোগ্য করি, দূরে কোথাওএর যোগ্য করি। দুঃখ ভোলার যোগ্য করি। স্বাধীনতার স্বাদ নেওয়ার যোগ্য করি। আমাকে বিমান বন্দরে পৌঁছে দিয়ে যান ছোটদা। সবাই জানে আমি একাই যাচ্ছি ভারতে, কলকাতায় অতসী নামের এক বন্ধু আছে আমার, ওর বাড়িতে থাকব, ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়াব। গোপন ব্যপারটি আমি পুষে রাখি নিজের ভেতর। প্রকাশ করলে সর্বনাশ। যদি বলি মিলন নামে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছি, দূরে হারাতে যাচ্ছি, আমার পায়ে শেকল পরাতে ব্যস্ত হবে সবাই। পরপুরুষের সঙ্গে দেশের ভেতর ঘুরি ফিরি ক্ষতি নেই, সীমানা ডিঙোনো চলবে না। শীতলক্ষার পাড়ে যদি দুজন বসে থাকতে পারি, গঙ্গার ধারে নয় কেন! গঙ্গার ধারে নয়। শীতলক্ষা আর গঙ্গা এক নয়। শীতলক্ষায় সাঁতার কাটো আর যাই কর, রাত্তিরে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরবে, গঙ্গার ধারে হাওয়া খেলে রাত ভেসে যাবে হাওয়ায়। রাতকে সবার ভয়। রাতকে আমারও ভয়। তাই কলকাতায় হোটেলে পৌঁছে আমি আলাদা ঘরের কথা বলি। দুজনের দুটো ঘর। কলকাতার হোটেলে দুঘরে দুজন। দিল্লির হোটেলেও, আগ্রাতেও। টই টই করে দু বন্ধু ঘুরে বেড়াচ্ছি সবখানে। পর্যটকের মত দেখে আসছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লাল কিল্লা, ইন্ডিয়া গেট, তাজমহল। হাতে হাত ধরে বিকেলের মিঠে হাওয়ায় হাঁটতে হাঁটতে একদিন বেশ ভাল বুঝি যে যে মিলনকে আমি ভালবাসি। ভালবাসি বলেই রাজধানী এক্সপ্রেসে অমন করে নিজের গলার সোনার চেইনটি খুলে মিলনের গলায় পরিয়ে দিই। ভালবাসি বলে এমন মনে হতে থাকে যে সে যদি আমাকে বলে হিমালয়ের চুড়ো থেকে লাফ দাও, তাই দেব। মিলনকে আমি আমার কষ্টের গল্পগুলো, সুখের গল্পগুলো বলতে চাই, বড় ইচ্ছে করে তার চোখে চোখ রেখে, চোখের পাতায় আলতো চুমু খেয়ে তাকে যে ভালবাসি তা বলি। আমার বলা হয় না কিছুই। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই জম্মুতে আমাকে গভীর করে স্পর্শ করে মিলন, যে স্পর্শ আমাকে আমূল কাঁপায়। শ্রীনগরের ডাল লেকে রাজকীয় একটি হাউজবোটে চেনা শহর থেকে চেনা মানুষের ভিড় থেকে বহু দূরে আগুন পোহাতে পোহাতে ভালবাসার জলে ডুবি। রুদ্রর সঙ্গে সম্পর্ক অনেকদিন শেষ হয়েছে আমার। দীর্ঘকাল পুরুষস্পর্শহীন এই শরীরে এত তৃষ্ণা ছিল, বুঝিনি। আমার শরীর জেগে ওঠে শুভ্র বিছানায়। সে শরীরকে সুখের চাদরে ঢেকে দেয় মিলন। ভেতরে যে সংষ্কার ছিল আমার, স্বামী নয় এমন কারও সঙ্গে মৈথুন সঙ্গত নয়, সেটি শালিমার বাগানের ঝড়ো হাওয়ায় তুলোর মত উড়ে যায়। মিলনের চেয়ে আপন এ জগতে কেউ নেই আমার, এরকম মনে হয়। আমি ভুলে যেতে থাকি মিলনের আলাদা একটি জীবন আছে। কলকাতায় ফিরে সে কথা স্মরণ হয় যখন সে তার বউ বাচ্চার জন্য ট্রেজার আইল্যান্ড থেকে শাড়ি গয়না কিনতে যায়। মিলনের আলাদা একটি জগত আছে, সে জগতে আমি কেউ নই তা স্মরণ হয় যখন সে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি যাবে বলে এবং একা যাবে বলে এবং যায়। ইয়াসমিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর যেমন একা লেগেছিল, মনে হয়েছিল খাঁ খাঁ করছে পুরো শহর, পুরো পৃথিবী, তেমন লাগে আবার।
আধঘন্টার উড়ান দূরত্ব কলকাতা থেকে ঢাকা। আধঘন্টা শেষ হচ্ছে, কিন্তু মিলন আমাকে বলছে না আবার কবে কোথায় আমাদের দেখা হবে, কবে আমাদের মিলন হবে আবার, বলছে না আমাকে সে ভালবাসে। কিছুই বলছে না। সুখী মুখ তার, বাড়ি ফিরছে। দীর্ঘশ্বাস গোপন করি আমি, অসহায় মেয়েমানুষ, ভালবাসার ফাঁদে পড়া আমি অবুঝ শিশুর মত হাত রাখি সুখী পুরুষটির হাতে। যদি আমার এই ষ্পর্শ তাকে এতটুকু বোঝাতে পারে ভেতরে কষ্ট আমাকে কেমন মুচড়ে নিচ্ছে। মিলন বলে, ‘এ কি! এমন করছ কেন?’
আকুল চোখে তাকাই ওর দিকে।
মিলন ভ্রু কুঞ্চিত করে বলে, ‘ও, তোমার বুঝি ভয় লাগছে? প্রথম চড়েছো তো বিমানে, তাই। এরকম হয়।’
ধীরে ধীরে আমার হাতটি তার হাত থেকে সরিয়ে নিই।
ঢাকায় নেমে মিলন একটি বেবি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যায় পুরোনো ঢাকায় ওর বাড়িতে। আমি নতুন ঢাকায়, নয়াপল্টনে। মিলন যখন বিদায় নিচ্ছে, তার মুখ দেখে মনে হয়নি অনেকগুলো দিন সে আমার সঙ্গে ছিল, মনে হয়েছে এই বুঝি হঠাৎ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এক অল্প-চেনা মেয়ের সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা হয়েছে।
এদিকে বইমেলা শুরু হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখি মিলন তার বউ নিয়ে মেলায় ঘুরছে। ট্রেজার আইল্যান্ড থেকে কেনা শাড়ি বউএর গায়ে। আমি অষ্পৃশ্য পড়ে থাকি দূরে, বহু দূরে।
এত কিছুর পরও মিলন-মোহ আমার সম্পূর্ণ দূর হয়নি। কিছুটা বাকি ছিল দূর হতে। একদিন মৌচাকের মোড় থেকে আমাকে এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে শরীরে মধু যেটুকু ছিল সেটুকুই শুধু শুষে নিয়ে চলে গেল মিলন, তার সময় ছিল না প্রেমের গুঞ্জনে পুরোটা দিন পার করার আমার রিনিকি ঝিনিকি সাধটির দিকে একবার তাকানোর। সাধের গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেদিন চোখের পুকুরে ভাসিয়ে দিই আমি।
০৭. আমরা এমনি এসে ভেসে যাই
অবকাশ থেকে খুব দূরে নয় মহাকালি ইশকুল। ইয়াসমিন হেঁটেই চলে যায় ওখানে শুক্রবারে। ছুটির দিন ইশকুলে আনন্দধ্বনির গানের ইশকুল বসে, সকলে সমস্বরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। ছোট বড় যে কোনও বয়সের মানুষ, কারও জন্য না নেই গানের ইশকুলে। পাঁচ বছর বয়সী আছে, আবার পঁচাত্তরও আছে। আমার খুব আনন্দ হয় দেখতে যে ইয়াসমিন চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে। আমার খুব আনন্দ হয় দেখে যে ও চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করে, আমার কাছ থেকে তালিম নিয়ে আমাকে অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে। সকাল কবিতা পরিষদে এখন ইয়াসমিনই সবচেয়ে ভাল আবৃত্তিশিল্পী। আমার অহংকার হয় ইয়াসমিনের জন্য। ও খুব ভাল একজন রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবে, আমি ওকে শান্তিনিকেতন পাঠাবো গান শিখতে, এরকম একটি তিরতির নীলাভ স্বপ্নের জলে আমি রাজহাঁসের মত সাঁতার কাটি। ইয়াসমিন আমার স্বপ্নের কথা জানে। নিজের জীবনের চেয়ে ইয়াসমিনের জীবনটিকে সুন্দর সুচারু করে তৈরি করতে যা কিছুৃ প্রয়োজন, আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি করার জন্য। পরিবার পরিকল্পনা আপিসে কাজ তেমন কিছু নেই আমার, বাড়িতেই বেশি কাটে সময়, ইয়াসমিনই হয়ে ওঠে আমার সবচেয়ে দীর্ঘক্ষণের সঙ্গী, সবচেয়ে বড় বন্ধু। কেবল বাড়িতে নয়, বাড়ির বাইরে গেলেও ইয়াসমিন। ওকে সঙ্গে নিয়ে শহর ঘুরে বেড়ানো, ময়মনসিংহ অসহ্য হয়ে উঠলে ঢাকায় সুহৃদকে দেখতে চলে যাওয়া, সাহিত্য আর সংস্কৃতি প্রাঙ্গণে কিছু হাঁটাহাঁটি করে সময় কাটিয়ে একসময় গীতার আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে আবার অবকাশে ফেরা। আমাদের এই বন্ধুত্বের মধ্যে অলক্ষ্যে এক সীমানা থাকে। আমরা কেউই ভুলেও এই সীমানা পার হই না। আমি যেমন কোনওদিন ইয়াসমিনকে বলিনি আমি কেন রুদ্রকে ছেড়ে এসেছি। ইয়াসমিনও বলে না হঠাৎ হঠাৎ ও কেন দেরি করে বাড়ি ফেরে। শুদ্ধ জীবন যাপন করতে গিয়ে কোনও অশ্লীলতাকে অন্তত দুজনের মধ্যে আমরা ঠাঁই দিই না। কিন্তু অশ্লীলতার সংজ্ঞা ইয়াসমিনের কাছে সম্ভবত আরও বেশি সংকীর্ণ, তাই সে ক্লাসের দুটো ছেলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে এসে আমাকে বলে বান্ধবী রিংকুর বাড়িতে গিয়েছিল। দুটো ছেলের সঙ্গে ক্লাসের পরে দুটো কথা বললে শুদ্ধতা কিছু কমে যায় না, কিন্তু আমি যদি ভুল ব্যাখ্যা করি সে আড্ডার, আমি যদি পছন্দ না করি, আমি যদি রুষ্ট হই, তাই ও গোপন রাখে। আমি যে ওকে ওর কোনও ছেলে বন্ধুর সঙ্গে মিশতে দিই না, তা নয়। ওর ছেলেবন্ধুরা আসে অবকাশে, ওদের সঙ্গে বসে ও গল্প করে। আমিও বসে গল্প করি। এত কাছের মানুষ আমি ওর অথচ এই দূরত্বটুকু কিছুতেই ডিঙোতে পারে না। আমাকে ভাল যেমন বাসে ও, ভয়ও তেমন পায়। ও ক্রমাগত আমার বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে মিশতে, আমার পরমর্শ মত আমার পছন্দ করা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে, আমি যে গান পছন্দ করি, যে জীবন পছন্দ করি, সেই গান গাইতে গাইতে, সেই জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করতে করতে আমি বুঝি না যে ও হাঁপিয়ে উঠছে। আমি বুঝি না যে ওর ভেতরে নিজের অস্তিত্বহীনতা দেখা দিচ্ছে। আমার মান সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি যত অল্পই হোক, তা নিয়ে যে আমি যেমন ইচ্ছে বাঁচি, আর ওর যে আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়, ওর নিজের স্বাধীনতা যে আমার ইচ্ছের কাছে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে, তা অনুভব করে যে ওর ভেতরে একটি নিঃসঙ্গতা জন্ম নিচ্ছে, আমার বোঝা হয় না। আমার সৌন্দর্য আর আমার বিস্তৃত শিল্পিত ভূবন ও সারাক্ষণই দেখছে আর ওকে আমার এই ভূবনে টেনে এনে আমি রানী হয়ে বসে থেকে বুঝি না ও যে নিরীহ একটি প্রজার চরিত্রে কেবল। প্রজাটিকে আমি ভালবাসি, ওকে যা আমার মনে হয় যে ওর প্রয়োজন উদারহস্তে দান করি কিন্তু ওর নিঃসঙ্গতাকে টের পাই না। আমি যে ওকে আর দশটা মেয়েমানুষের মত লেখাপড়া শেষ করে যাকে তাকে বিয়ে করে যে কোনও গৃহবধু হতে দিতে চাইছি না, আমি যে ওকে ওর স্বকীয়তা, ওর নিজস্ব সৌন্দর্য শিল্প নিয়ে বিকশিত হওয়ার জন্য আলোকিত হওয়ার জন্য বিষম চাইছি তা বোঝে ও, বুঝেও হীনমন্যতায় ভোগে, আমার জানা হয় না যে ভোগে। এত কাছে থেকেও, এক বিছানায় দুজন ঘুমিয়েও ওর ক্ষত আমার দেখা হয় না। অবকাশে বাবার হিংস্রতা, দাদা আর তাঁর বউএর স্বার্থপরতা, মার উদাসীনতা সব কিছু থেকে ইয়াসমিনকে বাঁচিয়ে যে একটি সুস্থ সুন্দর পরিবেশ দিতে চাইছিলাম, তা আমি জানি না যে ব্যর্থ হচ্ছে।
ইয়াসমিন এক রাতে বাড়ি ফেরে না। রাত গভীর হতে থাকে, বাড়ি ফেরে না। শহরে ওর যত বন্ধু বান্ধবী আছে সবার বাড়িতে গিয়ে খুঁজি, না ও নেই। ওর চেনা পরিচিত কারও বাড়িতেই ও নেই। আত্মীয়দের বাড়িতেও খুঁজি, নেই। রাত পার হয়, আমি আর মা নির্ঘুম রাত পার করি। বাবা সারারাতই পাঁয়চারি করেন ঘরে। কোথায় হারাবে মেয়ে? অন্যদিনের মত কলেজে গেছে, কলেজ থেকে দুপুরে না হোক বিকেলে বাড়ি ফেরে, সেখান বিকেল পেরিয়ে রাত পেরিয়ে ভোর হতে যাচ্ছে, ইয়াসমিনের কোনও খবর নেই। আশঙ্কায় আমি নীল হয়ে থাকি। মার দুচোখ বেয়ে অবিরল জলের ধারা, তিনি মেঝেয় জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজের পর নামাজ পড়ে যাচ্ছেন আর আল্লাহর কাছে মেয়েকে যেখানেই রাখেন হেফাজতে রাখার অনুরোধ জানাচ্ছেন। ভোরবেলা থেকে কালো ফটকের সামনে বসে আছি, সকাল কেটে যায়, দুপুর পার হয়, ইয়াসমিন ফেরে না। বাবা বার বার চেম্বার থেকে ফোন করছেন বাড়িতে ইয়াসমিন ফিরেছে কি না জানতে। মা বুড়া পীরের মাজারে গিয়ে কিছু একটা মানত করে আসেন। আমার শ্বাস কষ্ট হতে থাকে দুর্ভাবনায়। আমার আর চিন্তা করার শক্তি থাকে না কোথায় ও যেতে পারে। রাত যখন নেমে আসে, রাত নেমে রাত বাড়তে থাকে, তখন খবর আসে ইয়াসমিন সানকিপাড়ায়, ওর ক্লাসে পড়ে ছেলে মিলনের বাড়িতে। খবরটি ঈশান চক্রবর্তী রোডে থাকে জাহাঙ্গীর নামের ইয়াসমিনের চেনা একটি ছেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দাদাকে নিয়ে আমি ছুটি সানকিপাড়ায় ওকে নিয়ে আসতে। একটি বিছানায় হাঁটুতে মাথা গুঁজে ও বসে ছিল। কি হয়েছে ইয়াসমিনের! আমি দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরলে ও এক ঝটকায় ওর হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে ‘ছুঁয়ো না আমারে!’
ছোঁবো না, হয়েছে কী! কেউ কিছু বলেছে! রাগ কেন!
‘চল বাসায় চল।’
‘না।’
এ কেমন উত্তর!
ইয়াসমিনের বক্তব্য মিলনের বড় ভাই মানু যা জানায় তা হল ইয়াসমিন মিলনকে বিয়ে করতে চায়। এক্ষুনি যেন আমরা ওকে মিলনের সঙ্গে বিয়ে দিই। হতবাক আমি জীবনে আর কখনও এভাবে হইনি! আমি বাকরুদ্ধ বসে থাকি। মিলনের সঙ্গে কোনওরকম প্রেমের সম্পর্ক ওর নেই এ ব্যপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু কী কারণে বিয়ের মত একটি অশালীন শব্দ ইয়াসমিন উচ্চারণ করতে পারে আর এমন অসভ্যের মত বিয়ের আবদার করছে আমি বুঝতে পারি না। ইয়াসমিন ঘোষণা দিয়ে দেয়, ও আর অবকাশে ফিরবে না। ফিরবে না তো ফিরবেই না। টেনে হিঁচড়ে তো নেওয়া সম্ভবই নয়, আদর করে বুঝিয়েও কোনও কাজ হয় না। শরীর লোহার মত শক্ত করে রেখেছে, মনটিকেও জানি না কি দিয়ে পিটিয়ে লোহা বানিয়ে নিয়েছে। ওর সব কিছু বড় অদ্ভুত লাগে। আজ ওর কাছে আমি বা দাদা কেউ নই, মিলন সারাক্ষণই বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল মাথা নিচু করে, যখন ভেতরের ঘরে এই নাটক ঘটছিল। ইয়াসমিন বেরিয়ে ছিল গতকাল জামা পাজামা পরে, এখন পরে আছে নীল একটি শাড়ি। শত ভেবেও আমার মাথায় কিছু ঢোকে না কি ঘটেছে, কি কারণে ও এমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে। মানুর কাছে জিজ্ঞেস করে কোনও উত্তর পাই না। দাদা ইয়াসমিনকে বুঝিয়ে বললেন, ‘বিয়ে তো এভাবে হয় না, এখন বাড়ি চল, পরে বিয়ের ব্যবস্থা হবে।’ আমিও বললাম, ‘এই মিলনকেই যদি তোর বিয়ে করতে হয়, ঠিক আছে লেখাপড়া শেষ কর, পরে ওকেই বিয়ে কর।’ ইয়াসমিন তিন দিন সময় দেয়, তিন দিনের মধ্যেই যেন ওর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয় মিলনের সঙ্গে। আমি হু হু করে কাঁদলাম বাড়ি ভর্তি লোকের সামনে। ইয়াসমিন আমার কান্না দেখেও মত পরিবর্তন করেনি। মধ্যরাত পার হয়ে যায় কেবল বিয়ের ব্যপারটির মিমাংসা করতে। ইয়াসমিনের ঘোষণা আমার নিজের কানে শোনা হয় না, ও মিলনের ভাই বোনের কাছে বলেছে ওর যা বলার। ওরাই এখন আপন ওর, যা কিছু ও জানাতে চাইছে, জানাচ্ছে ওদের দিয়ে। আমাকে সরাসরি ও কিছু বলে না। ওর কেন হঠাৎ আমার ওপর এই রাগ, আমি বুঝে পাই না। কী এমন ঘটেছে, আমি কী করেছি যে আমার ওপর এই রাগ! রাতে আমার আর অবকাশে ফেরা হল না। দাদা ফিরে গেলেন। আমি রাতটুকু ওর পাশে শুয়ে আরও একটি নির্ঘুম রাত কাটালাম। রাতে যতবারই চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছি কি ঘটেছে যেন আমাকে বলে ও, যতবারই আমি ওর কাঁধে বা হাতে আলতো করে হাত রেখেছি, ও আমার হাত সরিয়ে দিয়েছে শক্ত হাতে। ও নিজেও ঘুমোয়নি। নাটকটির পেছনে কোনও রহস্য আছে, আমি নিশ্চিত। পরদিন সকালে ইয়াসমিনকে অবকাশে ফিরিয়ে নিয়ে আসি কথা দিয়ে যে বিয়ে মিলনের সঙ্গেই ওর হবে, আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু। এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না ওকে বাড়ি নিয়ে আসার। সারা পথ ও আমার সঙ্গে কোনও কথা বলে না। আমার চোখের দিকে তাকায় না। এরকম পরদিনও। সারাদিন শুয়ে থাকে দেয়ালের দিকে মুখ করে। দাদা বাড়ি এলে চেঁচিয়ে নির্লজ্জের মত নিজের বিয়ের কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার সহস্র প্রশ্নের একটি উত্তরও ও দেয় না। বলে না কি হয়েছে ওর, যে রাতে বাড়ি ফেরেনি, কোথায় ছিল সে রাতে, বলে না। কী এমন ঘটেছে যে মিলনকে ওর তিনদিনের মধ্যেই বিয়ে করতে হবে, বলে না। রহস্যের কোনও কূল কিনারা আমি পাই না। বাড়ির কেউই পায় না। পরে, অনেক বছর পর যখন নিজের স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করছে ইয়াসমিন, যখন ওর সেই বয়সের আড়ষ্টতাগুলো দূর হয়েছে, বলেছে কি ঘটেছিল সে রাতে। একই ক্লাসে পড়া বন্ধু-মতো ছেলে মিলন তার বড় ভাইয়ের মোটর সাইকেল চালিয়ে কলেজে গিয়েছিল। ক্লাস শেষে মিলন ইয়াসমিনকে আমন্ত্রণ জানায় মধুপুরে বেড়াতে যাওয়ার। ইয়াসমিন না করেনি। মোটর সাইকেলের পেছনে বসে দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ব্যপারটি স্পষ্টতই লোভনীয়। মধুপুরে বোটানির ছাত্রছাত্রী গাছপালা দেখতে দেখতে জঙ্গলে হাঁটে। কোন গাছের কি নাম, কোন পাতায় কি অসুখ তা বলতে বলতে, কিছু পাতা আর শেকড় তুলে জমাতে জমাতে মধুপুর কটেজের দিকে হেঁটে যেতে থাকে যেখানে মোটর সাইকেলটি দাঁড় করানো। কটেজ পর্যন্ত পৌঁছোয়নি, তখনই একটি পেটমোটা পুলিশ এসে দুজনকে থামতে বলে। পেটমোটা ওদের দিকে বাঁকা হাসি ছুঁড়ে বলল, ‘কি করস তরা এইখানে!’ ওরা জানালো যে ওরা কলেজে পড়ে, কলেজ থেকে এখানে এসেছে ঘুরে ঘুরে গাছপালা দেখতে। পেটমোটা বিকট হাসি হাসে। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে কেউ আসছে কি না, খেঁকিয়ে ওঠে, ‘পাঁচ হাজার টাকা দে।’ পাঁচ হাজার টাকা কেন দিতে হবে এ কথাটি জিজ্ঞেস করার আগেই পেটমোটা বলে, ‘জঙ্গলে অবৈধ কাজ করতে আইছস, টাকা না দিলে এইখান থেইকা যাইতে পারবি না।’ ওরা অস্বীকার করল, কোনও রকম অবৈধ কাজ করার উদ্দেশে ওরা আসেনি। পেটমোটা কান দেয় না ওদের কথায়। ইয়াসমিনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলে, ‘ছেড়ি তো বাজারের ছেড়ি, দেইখ্যাই তো বুঝা যাইতাছে।’ না, দেখে তা মনে না হলেও পেটমোটা বলল তা। মিলন বলল তার হাতে টাকা নেই, টাকা নিয়ে আসতে তার শহরে যেতে হবে। পেটমোটা খপ করে ইয়াসমিনের হাত ধরে মিলনকে বলে, ‘যা শহরে, তুই যা, এইটারে রাইখা যা।’ইয়াসমিন পেটমোটার খসখসে শক্ত হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে চেয়ে ব্যর্থ হয়। মিলনের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলে, ‘মিলন তুমি যাইও নাঞ্চ। করুণ চোখে তাকিয়ে অনেকে অনেক কিছু আবদার করে, কিন্তু সেই আবদার সবাই রাখে না। নিজের কথা ভাবে। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে যে একটি কথা আছে, তা মিলন জানে না তা নয়, জানে। মিলনের ওপর এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সে ইয়াসমিনকে এই জঙ্গলে এক বদমাশ পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে কী না। মিলন চলে গেলে টাকা নিয়ে সে ফিরুক না ফিরুক, পুলিশ ইয়াসমিনকে অক্ষত অবস্থায় রাখবে না। হয়ত ওকে ধর্ষণ করে ফেলে রেখে উধাও হয়ে যাবে জঙ্গলে। লজ্জায় শরমে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও পথ থাকবে না ওর। চোখ কান নাক মুখ বন্ধ করে এরকমই ভাবছে ইয়াসমিন। মিলনের একটি হাত মোটর সাইকেলে, আরেকটি হাত কোমরে, কোমরের হাতটি যদি মোটর সাইকেলের হাতল স্পর্শ করে, যদি করে এই ভয়ে ইয়াসমিন চোখ খোলে না। আশঙ্কায় কাঁপছে ও ভেতরে, বধির হতে চাইছে যেন ওকে শুনতে না হয় মোটর সাইকেল স্টার্ট হওয়ার কোনও ভয়ংকর শব্দ। ইয়াসমিনের অনুরোধ মিলন না রাখতেও পারত। মোটর সাইকেলে চড়ে দিব্যি চলে যেতে পারত পেছনে কি হবে না হবে তার কিছুই না ভেবে, পুলিশ তো তাকে ছেড়েই দিয়েছে। হ্যাঁ মিলন চলে যেতে পারত, ইয়াসমিন তার কোনও প্রেমিকা নয় যে ঝাঁপিয়ে পড়বে বিপদ থেকে ওকে উদ্ধার করতে। কিন্তু মিলন যায়নি। না সে যায়নি। পুলিশকে বলেছে, ‘মোটর সাইকেল রাইখা দেন, আমাদেরে যাইতে দেন, শহর থেইকা টাকা নিয়া আসি।’ নাহ, মোটর সাইকেল পুলিশ রাখবে না, রাখবে ইয়াসমিনকে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলে সে যা ইচ্ছে তাই করবে ওকে। কারও অনুমান করতে অসুবিধে হয় না কী করবে। ইয়াসমিন ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিশের মুহূর্মহু আদেশেও মিলন জিম্মি হিসেবে একা ইয়াসমিনকে রাখতে দেয়নি। মিলন যখন স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে সে যাবে না, হারিয়ে যেতে থাকা জীবনটি ইয়াসমিন হাতে পেল, কৃতজ্ঞতায় সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর সত্যি সত্যি যখন একসময় সন্ধে নামল, ঝুপঝুপ করে অন্ধকার ঝরে জঙ্গল কালো হয়ে গেল, পুলিশ ওদের দুটিকে নিয়ে বনবিভাগের এক কর্মকর্তার বাড়িতে ঢুকিয়ে বলে এল, কাল সকালে গুণে গুণে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যেন ওরা বেরোয়। মোটর সাইকেল জমা রইল পুলিশের কাছে। সেই বাড়িতে ইয়াসমিনের নাম ঠিকানা যখন জিজ্ঞেস করা হয়, বিবর্ণ মুখে ইয়াসমিন বাবার নাম আবদুর রফিক, পেশা ব্যবসা, ঠিকানা কাঁচিঝুলি বলে নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখে দুহাতের দু মুঠির মধ্যে। রাখে কারণ নিজের বাবা স্বনামধন্য ডাক্তার রজব আলীর মুখে ও চুন কালি দিতে চায় না। মেয়ে রাতে বাড়ি ফেরেনি, কোনও এক ছেলেসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, এর চেয়ে বড় কলঙ্ক একটি মেয়ের জীবনে আর কী হতে পারে! ইয়াসমিন সারারাত ঘুমোয় না। ওকে ঘুমোতে দেওয়া হয়েছে বাচ্চাকাচ্চাদের ঘরে। সারারাত বারান্দার একটি ঘরে মিলনও না ঘুমিয়ে কাটায়। মিলন কর্মকর্তার বাড়ি থেকে এক বন্ধুকে ফোন করে দিয়েছে যেন খুব সকালে পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করে মধুপুরের বনবিভাগের কর্তার বাড়িতে আসে। সকালে বন্ধু টাকা নিয়ে এলে সেই টাকা পুলিশকে দিয়ে মোটর সাইকেল ফেরত নিয়ে দুজনে ফেরে শহরে। শহরে তো ফিরল, এখন কী হবে! কলঙ্ক যাবে কোথায়! এক রাতের কলঙ্ক মোচন করবে ইয়াসমিন কী করে! মিলন পরামর্শ দেয়, এই মুহূর্তে বিয়ে ছাড়া এই কলঙ্ক থেকে মুক্তির কোনও উপায় নেই। ইয়াসমিন রাজি হয় না। অবকাশের কাছেই ওর চেনা সেই জাহাঙ্গীর ছেলেটির বাড়িতে উঠল, সারাদিন ভাবল অবকাশে ফিরবে কী ফিরবে না। ফিরলে সকলে ঘিরে ধরবে, জিজ্ঞেস করবে কাল রাতে কোথায় ছিল ও। কী উত্তর দেবে! ও তো নানির বাড়ি ছিল না, কোনও খালার বাড়িতে ছিল না, কোনও বান্ধবীর বাড়িতে ছিল না। ছিল না যে এসব কোনও বাড়িতে, তা তো অবকাশের সকলে কাল রাতেই জেনে গেছে নিশ্চয়ই। জাহাঙ্গীরের বাড়ি থেকে অবকাশের কালো ফটকের সামনে এসে সন্ধেবেলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে। ঢুকবে কি ঢুকবে না করেছে। অপেক্ষা করেছে, কিসের অপেক্ষা ও নিজেই জানে না। কোনও আলো এসে ওর রাতের কলঙ্ক মোচন করার অপেক্ষা! কোনও জাদু বলে জীবনকে একটি রাত পিছিয়ে নিতে পারার অপেক্ষা! না, কিছুই গতরাতের নিখোঁজ হওয়া মেয়ের কলঙ্ক মোচন করে না। এরপর নিজের ওপর ধিককার ওকে মিলনের বাড়িতে নিয়ে নাটকটি ঘটায়। মুখ দেখাতে তখনও ও পারেনি, তাই হাঁটুতেই গোঁজা ছিল মুখ। নাটকের যবনিকা পতন হওয়ার পর অবকাশে ফিরেছে বটে, গোঁজা মুখটি তুলেছে বটে, কিন্তু চোখ কারও চোখে পড়তে দেয় না, চোখ হয় দেওয়ালে, নয়ত কড়িকাঠে। ও যেন এ বাড়ির কেউ নয় আর, সেই আগের ইয়াসমিন ও নয়, এ বাড়ির কণিষ্ঠা কন্যা ও নয় আর। দেখে এত মায়া হয় আমার, মায়া হয় আবার রাগও হয়। শত জিজ্ঞাসাতেও যখন ও মুখ খোলে না, বলে না কী ঘটেছে যে এমন হুট করে বিয়ে করতে হবে ওর, আমি দরজার চৌকাঠে বসে সন্ধের আঁধার আঁধার উঠোনের দিকে তাকিয়ে, যেন বিছানায় শুয়ে থাকা ও শুনতে পায়, মুখ এদিকে না ফেরালেও, বলি ‘জীবন কিন্তু একটাই, যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘইটা থাকে ওই রাত্রে, তাইলে কী হইছে এমন! মানুষের জীবনে কত দুর্ঘটনাই ত ঘটে, এইল্লিগা বিয়া করতে হইব? তর সাথে কী সম্পর্ক মিলনের? যদি ওর সাথে গোপনে গোপনে প্রেম কইরা থাকস, যদি ওরে ছাড়া না বাচস, তাইলে যা, বিয়া কর। বিয়া করার শখ হইছে বিয়া কর। কিন্তু একটা জিনিস মরে রাখিস, বিয়া করার সিদ্ধান্ত হুট কইরা লওয়া বালা না। নিজে আগে লেখাপড়া শেষ কইরা চাকরি কর। তারপর ত বিয়া। নিজের পায়ে দাঁড়া আগে। কারও ওপর ডিপেণ্ডেন্ট হইস না। বোটানিতে মাস্টার্স কর। পিএইচডি কর। টিচার হ। তুই তো এগ্রিকালচার ইনিভার্সিটির টিচার হইতে পারবি। বিয়া করার শখ হইছে, তাইলে মিলন কেন? ও কী জানে? কী পারে? শুদ্ধ কইরা ত একটা বাক্যও কইতে পারে না। তার ওপর মানুর ভাই ও। অমন শয়তানের ভাই আর কত ভাল হইব! কত ভাল ভাল ছেলেরা আসে এই বাড়িতে। তাদেরে কাউরে পছন্দ কর। আমার অনেক ডাক্তার বন্ধুই তো তরে বিয়া করার সুযোগ পাইলে ধন্য হইয়া যাইব।’
আমার যে ভয়টি ছিল যে মিলনের সঙ্গে ইয়াসমিনের বিয়ের ব্যবস্থা না করলে ভয়ংকর কোনও নাটক ও ঘটাবে অবকাশে, কিন্তু আমার সেই ভয় দূর করে দিয়ে দেখি ও হঠাৎ ঠিক আগের ইয়াসমিন হয়ে উঠল। বাড়িতে ওর বান্ধবীরা আসছে, বান্ধবীদের বাড়িতে ও যাচ্ছে। বিয়ে তো দূরের কথা, মিলনের ফোন এলে ও বলে দেয় ও কথা বলবে না। কথা অবশ্য একদিন বলল, কড়া কণ্ঠে বলে দিল, বাড়ি থেকে ওর বিয়ে ঠিক করা হয়েছে, মিলন যেন আর ফোন না করে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে রানা নামের দেখতে সুন্দর একটি ছেলে আসে ইয়াসমিনের কাছে। ছেলেটি ইয়াসমিনের বান্ধবী কৃষ্টির বন্ধু রাকার বড় ভাই। রানার সঙ্গে বৈঠকঘরে বসে অনেকক্ষণ গল্প করে ইয়াসমিন। দেখে স্বস্তি হয় আমার। স্বস্তি হয় এই জন্য যে মিলনকে বিয়ে করার পাগলামো ওর দূর হয়েছে, আর মিলনের চেয়ে রানা ছেলেটি দেখতে শুনতে বিদ্যায় বুদ্ধিতে অনেক ভাল। রানা ফোন করলে দীর্ঘক্ষণ মিহি সুরে কথা বলে ও। রানা মাঝে মাঝে নিজে গাড়ি চালিয়ে এ বাড়িতে আসে, বুক ফুলিয়ে গাড়ির গর্বে ইয়াসমিনকে নিয়ে বেরিয়ে যায় এদিক ওদিক বেড়াতে। যায় কিন্তু পেট্রোলের টাকাটি ইয়াসমিনের কাছ থেকে নেয়। রিক্সাভাড়াও মাঝে মাঝে ওর কাছ থেকে নেয়। ইয়াসমিন হঠাৎই একদিন এই টাকা-লোভী রানার সঙ্গে হতে যাওয়া প্রেমটি চুকিয়ে ফেলে। নিয়মিত কলেজে যায়, ক্লাস শেষ হলে বাড়ি ফেরে। সকাল কবিতা পরিষদের আবৃত্তি আর আনন্দধ্বনির গানের উৎসবে মেতে থাকে। ওর শখের জিনিসপাতি, এমনকি প্রয়োজনেরও, বাবা যা দেন না বা দিতে চান না, দিই আমি। মিলনের সঙ্গে এক রাতের হাওয়া হওয়ার কলঙ্কটি ধীরে ধীরে মলিন হয়ে গেছে। কিন্তু একটি জিনিস ইয়াসমিনের মনে হতে থাকে, তা হল, কেউ ওকে পছন্দ করে না। বাড়িতে আমার চেনা পরিচিত বা বন্ধু যারাই আসে, ডাক্তার বন্ধু, সাহিত্যিক বন্ধু, আমার রূপ আর গুণের দিকে তারা তাকিয়ে থাকে দুচোখ মেলে, কেউ তো ইয়াসমিনের দিকে একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় না! এই মনে হওয়াটি নিয়ে ওর যে কষ্টটুকু ছিল তা কেটে যায়, যেদিন আতাউল করিম সফিক ওর দিকে তাকালো। সফিক আমার বয়সী, সুদর্শন যুবক, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ভদ্রতা আর অমায়িকতা, একনিষ্ঠ সাহিত্যকর্মী। সাহিত্যসেবা করেছে বলে অয়চ্ছল জীবনের পথে পা বাড়ায়নি। লেখাপড়া শেষ করে বিসিএস পাশ করে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে। ইয়াসমিনের জন্য সফিকের আগ্রহ আমাকে আশ্বস্ত করে। আমি ঠিক ইয়াসমিনকে লেলিয়ে দেওয়া বলতে যা বোঝায় তা দিইনি, তবে সফিক এসে যখন ইয়াসমিনকে খোঁজে আমি ওকে ডেকে দিই, ও যখন সফিকের সামনে যাওয়ার আগে ভাল একটি জামা পরে বা চুল আঁচড়ায় বা লিপস্টিক দেয়, আমি ধমকে বলি না ‘সাজস কেন! সাজার কী হইল! যেমনে আছস, অমনে যা।’ যখন দুজন বসে গল্প করে, আমি বলি না, ‘অত বেশি গপ্প করার দরকার নাই।’ হঠাৎ করে আমি যেন খুব উদাসীন হয়ে যাই। যে ঘরে বসে ওরা গল্প করে, সে ঘর থেকে কোনও একটি কাজের ছুতোয় আমি অন্য ঘরে চলে যাই। কাউকে বলি ও ঘরে চা নাস্তা কিছু দিয়ে আসতে অথবা নিজেই ট্রে সাজিয়ে নিয়ে যাই। সফিক চলে গেলে জিজ্ঞেস করি, ‘কি কইল সফিক!’ ইয়াসমিন মিষ্টি হেসে বলে, ‘কয় আমারে নাকি খুব সুন্দর লাগতাছে।’
‘আর কী কয়?’
‘কয় চল একদিন কোথাও বেড়াতে যাই।’
একদিন যখন সফিক ইয়াসমিনকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যেতে চাইল, ইয়াসমিন লাজুক হেসে ঘটনাটি জানালে আমি বললাম, ‘তা যা না, বেড়াইয়া আয়।’ আমার অনুমতি ইয়াসমিনকে সফিকের সঙ্গে বাইরে পাঠায়। অনুমতি দিই কারণ মিলনের মত একটি গবেট ছেলেকে বিয়ে করার ওর আবদারটি এখনও মাঝে মাঝে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত আমাকে ধারালো দাঁত নখ বের করে আঁচড় বসায়। তা না হলে আমি তো ছিলামই অন্যরকম, যে আমি কখনও ভুলেও ভাবিনি যে ইয়াসমিন আর আমি সারাজীবন এক সঙ্গে থাকবো না কেবল গান আর কবিতা নিয়ে। বিয়ের মত দুর্ভাবনা কখনই আমার মাথার আশে পাশেই ভিড়তে সাহস পেত না না যদি না সেদিনের ওই নাটকটি না ঘটত। বিয়ে করলে প্রেম করে বিয়ে করা ভাল, কোনও দুর্ঘটনায় পড়ে বা কোনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যেন সে বিয়ে না হয়। বাইরে থেকে ফিরে এলে ইয়াসমিনকে জিজ্ঞেস করি, ‘কই গেছিলি, কি কইল সফিক।’ ইয়াসমিন বলে ‘এগ্রিকালচারাল ইনিভার্সিটিতে নিয়া গেছিল।’ কি কইলর উত্তরে কাঁধ নেড়ে বলল, তেমন কিছু না। আমার জানার ইচ্ছে ছিল ‘তোমাকে ভালবাসি, চল আমরা বিয়ে করি’ এরকম কিছু একটা বলেছে কী না। সফিক সম্পর্কে জানতে চাইলে বাবা মাকে জানিয়ে দিয়েছি, ‘খুব ভাল ছেলে, এরকম ছেলে লাখে একজন। ছেলেডা ইয়াসমিনরে খুব পছন্দ করে।’ সাহিত্যিক এই গুণটি বাবা বা মার জন্য কোনও গুণ নয়। গুণ হল ভাল চাকরি করে ছেলে, সেটিই। কদিন পরই লক্ষ্য করি, সফিক ডাকলেও ইয়াসমিন আর কাছে যাচ্ছে না, আমার অনুরোধও ওকে সামান্য নড়াতে পারে না, আমি হাত ধরে টানতে নিলে আমার হাত থেকে নিজেকে সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, ‘ধুর আমারে ঠেইল্যো না তো! আমি যাইতাম না!’ কেন ও যাবে না সফিকের সামনে, কি ঘটেছে, ইয়াসমিন আমাকে কিচ্ছু জানায় না। পরে একদিন শুধু বলেছিল, ‘ব্যাডা শইলে হাত দিতে চায়।’
মানে? কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে আমার।
‘শইলে হাত দিয়ে চায় মানে!’
‘মানে আর কী!’
‘কী, হাত ধরতে চায়?’
‘হ।’
কানের ঝাঁ ঝাঁ কমতে থাকে। ‘হাত না হয় ধরলই। হাত ধরা তো এমন কিছু না।’ ইয়াসমিন সরে যায় সামনে থেকে। শরীর প্রসঙ্গে আমাদের কথপোকথন কখনও খুব এগোয় না কারণ একটি অদৃশ্য সুতোয় আমাদের ঠোঁটজোড়া বাঁধা। সেদিনের প্রশ্নের উত্তর হাত থেকে কোথাও প্রসারিত হয় না বা হতে চায় না।
ইয়াসমিন আমাকে বলে না সফিকের মত শিক্ষিত সজ্জন মূল্যবান রুচিবান সংস্কৃতিবান ছেলেকে এমন হেলা করছে কেন ও! অনেক অনেক বছর পর যখন স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করছে ইয়াসমিন তখন সফিকের প্রসঙ্গ উঠলে ও হেসেছে, হাসতে হাসতে বলেছে, দেবতার ভেতরের ভয়ংকর এক দানব দেখেছে ও। সেদিনের সেই অক্ষমতা আর কাউকে কিছু বোঝাতে না পারার অস্থিরতা ওকে যে যন্ত্রণা দিয়েছে, সেই যন্ত্রণার কথা মনে করে একটি কালো রেখা ফুটে উঠছিল ওর ফর্সা কপালে। ওর প্রতি সফিকের আগ্রহ ওকে অন্তত এইটুকু নিশ্চিতির উদ্ধার দিয়েছিল যে সফিকের সঙ্গে ওর বিয়ে হলে সংসারের সকলের মুখে হাসি ফুটবে, চুনকালির আশঙ্কা জন্মের মত দূর হবে। কিন্তু যখন সফিকের বলার কথা তোমাকে ভালবাসি, দুজনে কথা বলতে বলতে কোথাও কোনও খোলা বাগানে পাশাপাশি হাঁটার কথা, একসময় হাঁটতে হাঁটতে হাতে হাত রেখে নদীর ওপারের না ফুরোনো সবুজের দিকে তাকিয়ে আগামী দিনের স্বপ্নের কথা বলার কথা— তখন সফিক একটি খালি ঘরে ওকে নিয়ে হুড়োহুড়ি করে ওর বুক খামচে ধরতে চায়। কেবল তাই নয়, এরপর অবকাশ এক বিকেলে খালি পেয়ে ইয়াসমিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে, টেনে জানা খুলতে চেয়েছে, টেনে পায়জামা। ইয়াসমিন চিৎকার করে বারান্দায় ঘুমিয়ে থাকা সুফিকে জাগিয়ে তুলেছে, গালাগাল করে সফিককে বাড়ি থেকে বের করে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে বালিশে মুখ গুঁজে জন্মের কান্না কেঁদেছে। কেঁদেছে ভাবতে ভাবতে যে কেউ ওকে সত্যিকার ভালবাসে না, কেবল এই শরীরটির ওপর সবার লোভ, আর কিছু নয়। এই শরীর খুব সস্তা শরীর। যার কিμছু নেই ভালবাসার, তার শরীর বুঝি হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। কবিতা লেখে ছেলে কাজল শাহনেওয়াজ, যার হোস্টেলের ঘরে সফিক ইয়াসমিনকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই কাজল অবকাশে আমার সঙ্গে সাহিত্যের আলাপ করে চা বিস্কুট খেয়ে যাবার সময় ইয়াসমিনকে একদিন চোখ টিপে বলে গেছে আবার যেন ও একা তার হোস্টেলের ঘরে যায়। আবদুল করিমের কথাও ওর মনে পড়েছে। হাসিনার দুলাভাই আবদুল করিম অবকাশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে উঠেছে, প্রায়ই বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে আসে, মা সবাইকে যত্ন করে খাওয়ান দাওয়ান, সেই হাতির মত দেখতে আবদুল করিম ইয়াসমিনকে একা পেয়ে ফিসফিসিয়ে বলেছে সপ্তাহে একবার যদি শোয় ও আবদুল করিমের সঙ্গে এক হাজার টাকা করে পাবে, তাহালে মাসে চার হাজার টাকা কামাই হবে ইয়াসমিনের। ব্যাটার স্পর্ধা দেখে ইয়াসমিন তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। তাজ্জব হয়েছে কিন্তু বলেনি আমাকে। বলেনি এইজন্য যে কেন আমার ওপর এই ঝঞ্ঝাট আসে না, কেন ওর ওপরই শুধু, এ যদি আমাকে বিষণ্ন করে, ভাবায়! যদি আমি ওকেই দোষী বলে ভাবি। অথবা এতে যদি আরও ও যে কুরূপা-নির্গুণ তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ওই শঙ্কায় সম্ভবত অথবা লজ্জায় ও বলেনি, অন্যের অন্যায় দেখে নিজেরই যে লজ্জা হয় সেই লজ্জায় অথবা বলেনি কারণ আমি যে ওকে শুদ্ধ সুন্দর মেয়ে বলে মনে করি, সেই মনে করাকে ধাককা দিয়ে নোংরা ডোবায় ফেলতে চায় না, আমি যে ওকে নিয়ে চমৎকার স্বপ্ন দেখছি, সেই স্বপ্ন ও গুঁড়ো করে দিতে চায় না, আমার আদরের আহলাদের আকাঙ্খার বোনটিকে যেমন আমি জানি চিনি ভালবাসি, তেমনই থাকতে চায়, আমার প্রিয় প্রিয় গানগুলি গাইতে চায়, আমার প্রিয় প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করতে চায় ওর আশ্চর্য সুন্দর কণ্ঠে, ওকে নিয়ে আমার গৌরবের ওপর একতাল গোবর ফেলে দিতে চায় না। আমাকে ভালবাসে তাই ওর কোনও কষ্ট আমাকে দেখাতে চায় না যা দেখলে আমার কষ্ট হবে। আমার স্বপ্নকে গানে কবিতায় বাড়তে দেয়। আমার ইচ্ছের সুতোয় রঙিন ঘুড়ি বেঁধে দেয়। বেঁধে দিয়ে আড়ালে গিয়ে গোপনে চোখের জল মোছে।
মাস গড়াতে থাকে। জীবন গড়াতে থাকে জীবনের মত। ছোট খাটো সুখ দুঃখে বয়স বাড়তে থাকে অবকাশের। অবকাশের মানুষ তাদের সুখগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়, দুঃখগুলো একা একা গোপনে লালন করে। মার ডালিম গাছে ডালিম ধরেছে। মা খুশিতে বাগ বাগ করে বাড়ির সবাইকে খাওয়ালেন, একটি নিয়ে গেলেন নানির বাড়িতে ভাগ করে খাওয়াতে, সকলে খেয়ে বাহ বাহ করেছে মার গাছের ডালিমের। আনন্দে মা আরও দুটো ডালিম গাছের চারা এনে লাগালেন উঠোনে। মার আনন্দই দেখেছে সবাই, কেউ মার কষ্টগুলো দেখেনি। ইয়াসমিন অনার্স পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করেছে। কলেজের প্রফেসর নিশ্চিত, মন দিয়ে পড়লে ইয়াসমিন মাস্টার্সেও ফার্স্ট ক্লাস পাবে। বাড়ি এসে ইয়াসমিন সবাইকে জানিয়ে দিল ওর ভাল ফলের খবর। আনন্দ ভাগ করে দিল সবাইকে। সবাই বসে পরীক্ষার ভাল ফলের আনন্দ খেল। কেবল ইয়াসমিনের ভেতরের কষ্টগুলোর দিকে কারও নজর পড়ল না। কষ্টগুলো ওর একার। তারপর তো সেই দিনটি এল, ভয়াবহ সেই দিনটি। যে দিনটিতে আমি ময়মনসিংহে নেই, দুদিন আগে গিয়েছি ঢাকায় বই এর খবর নিতে। ফিরে এসে দেখি ইয়াসমিন বাড়িতে নেই। গতকাল ভোরবেলায় চলে গেছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না। একটি চিরকুট আমার টেবিলের ওপর।
বুবু, আমি যাচ্ছি। এ বাড়িতে আর ফিরব না। আমার খোঁজ কোরো না।
মা স্তব্ধ বসে ছিলেন।
‘কই গেছে ইয়াসমিন? কেন গেছে? কি হইছিল?’ চেঁচাই।
মা আমার চেঁচানোর বিপরীতে চেঁচান না। সারা গা আমার হিম হয়ে থাকে। বাবার বোনের মেয়ে ওরফে আমাদের ফুপাতো বোন ওরফে অবকাশের কাজের মেয়ে সুফি জানায় খুব ভোরে একটি কালো শাড়ি পরে ইয়াসমিন বেরিয়ে গেছে। মা অনেকক্ষণ পর মুখ খোলেন, ‘তর বাপে মাইরা ওরে রাখছে কিছু! যাইব না কেন? এই বাড়ি থেইকা যাওয়াই ভাল।’ মা ধীরে ধীরে চোখের জল ঝরাতে ঝরাতে বর্ণনা করেন গত রাতের ভয়াবহ বীভৎসতার — বাবা হয়ে কি করে নিজের বড় হওয়া মেয়েকে পাষণ্ডের মত চাবুক দিয়ে মেরেছেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একতিল জায়গা নেই যেখানে চাবুক পড়েনি। বাবার হাতে মুঠি মুঠি চুল উঠে এসেছে, এমন জোরে টেনেছেন চুল। এমন জোরে হিড়হিড় করে জামা ধরে টেনেছেন, জামা ছিঁড়ে গেছে। সারা গা লাল হয়ে ফুলে গেছে। কী দোষ ছিল ওর? ও ফিরেছে রাত বারোটায়, বাবা অস্থির পায়ে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছিলেন ইয়াসমিনের ফেরার অপেক্ষায়। কালো ফটকের কাছে একটি গাড়ি এসে থামলে দৌড়ে তিনি ফটকের কাছে দৌড়ে গিয়ে দেখেন ইয়াসমিন একটি গাড়ি থেকে নামল, যে গাড়িতে বসা ছিল দুটো ছেলে। বাবা যদি জানতে চাইতেন, ছেলে দুটো কে? জানতেন, ওরা প্রবীর আর শাকিল। ইয়াসমিনকে দিদি বলে ডাকে ওরা। দিদির মতই ওদের পরবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে ও, ওদের দুঃখে সুখে সঙ্গী হয়। হাঁটুর বয়সী প্রবীর আর শাকিল কোত্থেকে এক গাড়ি যোগাড় করেছে, আনন্দে নাচতে নাচতে ইয়াসমিনকে আবদার করেছে, দিদি চলেন ‘ঢাকা ঘুইরা আসি।’ কথা, সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরবে গাড়ি। প্রবীর জীবনে কখনও ঢাকা যায়নি। নাচতে নাচতে ইয়াসমিনও গেল। বিকেলেই ফিরত গাড়ি, কিন্তু ফেরার পথে গাড়ি গেল নষ্ট হয়ে। তাই মধ্যরাত। তাই চাবুক। তাই যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাওয়া। আমি মাঝখানে হিম হয়ে আছি। মাকে নিয়ে যখন বেরোই ওকে খুঁজতে, তখন বিকেল। প্রথমেই নানির বাড়িতে গিয়ে শুনি কাল রাতে নানির বাড়িতে ইয়াসমিন ছিল। খুব বিষণ্ন ছিল ওর মুখ। কাউকে বলেনি কী ঘটেছে বাড়িতে। কিছু যে ঘটেছে নানির বাড়ির কেউই ভাবেনি, ভেবেছে ইয়াসমিন শখ করে বুঝি নানির বাড়িতে একটি রাত কাটাচ্ছে। আজ দুপুরের দিকে পরনের কালো শাড়িটি খুলে রেখে হাশেম মামার মেয়ের একটি জামা পরে বেরিয়ে গেছে। আরও আত্মীয়দের বাড়িতে, বন্ধু বান্ধবীদের বাড়িতে খুঁজে দেখি কোথাও ও নেই। বাড়ি ফিরে আশায় থাকি রাতে হয়ত ফিরে আসবে। না, ও ফেরে না সে রাতে। পরদিনও আবার খোঁজাখুঁজি। টেলিফোনে খবর নেওয়া এ বাড়ি ও বাড়ি। কেবল ময়মনসিংহে নয়, ঢাকায় আত্মীয় বন্ধুদের বাড়িও খবর নেওয়া হয়েছে। নেই। পরদিন আসে। পরদিন যায়। একফোঁটা ঘুম নেই, একদানা খাওয়া নেই, একবিন্দু জলে ছোঁয়ানো নেই শরীর, উৎকণ্ঠার সমুদ্রে মাছের মত ডুবে আছি। ইয়াসমিন ফিরছে না। দিন আরেকটি পার হল। ও ফেরে না। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুর, ইয়াসমিনের ভাল বন্ধু, আসে খোঁজ নিতে। নিজেও বাড়ি বাড়ি যায় খুঁজতে। যে বাবা সবুরের দিকে কড়া চোখে তাকাতেন কখনও সামনে পড়লে, তাকে বাপ ডেকে জানতে চান কোথায় যেতে পারে মেয়ে। কোথাও না পেয়ে সবুর নিজে গিয়ে হাসপাতালে খুঁজে এলো, ওখানেও নেই। তিনদিন পর মিলনের বাড়ি থেকে খবর এল ফুলপুরে ওর ক্লাসের এক বন্ধু জামানের বাড়িতে আছে ও। ও নাকি মিলনকে বিয়ে করেছে। খবরটি রাতে এল। সারারাত আমি ঘরময় অস্থির হাঁটি আর নিজেকে প্রবোধ দিই বলে যে এ নাটক, আবার নতুন কোনও নাটকের আয়োজন করেছে ইয়াসমিন। দুঃসংবাদটি আর যা কিছুই হোক, যেন সত্য না হয়। হাসিনা ফুলপুরের মেয়ে, পথঘাট চেনে, ওকে সঙ্গে নিলে বাড়ি খুঁজতে সুবিধে হবে বলে ওকে নিয়ে ভোরবেলায় ফুলপুরে রওনা হলাম। ব্রহ্মপুত্র নদ পেরিয়ে মুড়ির টিন বাসে করে লোকের গা ধাককা খেতে খেতে ভাঙা রাস্তায় বাসের ওঠানামায় মাথায় বাসের ছাদের দেয়ালের ঠোকর খেতে খেতে লোকের ঘামের গন্ধ বাচ্চাকাচ্চার মলমুত্রবমির গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পৌছলাম ফুলপুর বাস স্টেশন। ফুলপুর বাজারে লোকদের জিজ্ঞেস করে করে জামানের বাড়ি কোথায় কোন পথে তা জেনে পথ হেঁটে অবশেষে একটি টিনের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। হাসিনা ভেতর ঘর থেকে খবর নিয়ে এল, ইয়াসমিন এ বাড়িতে আছে এবং ও বিয়ে করেছে মিলনকে, করেছে গতকাল। না, এ খবরটি আমি বিশ্বাস করতে চাই না। এ মিথ্যে খবর। কেউ আমাকে বলুক, বলুক যে খবরটি সত্যি নয়, আমি আশেপাশে তাকাই সেই কারও জন্য। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখি একটি অগোছালো বিছানায় দুটো বালিশ পাশপাশি, একটি বালিশের কাছে ইয়াসমিনের চুলের ক্লিপ। তবে কি এই বিছানাতেই মিলনকে নিয়ে শুয়েছে ও রাতে! বিয়ে কি সত্যি সত্যিই করেছে! আমার তবু বিশ্বাস হতে চায় না। এই মুহূর্তে বাড়ির ছাদ যদি ধ্বসে পড়ত মাথায়, এই মুহূর্তে যদি ব্রহ্মপুত্রের বন্যা ভাসিয়ে নিত এই পুরো ফুলপুর! প্রলাপের মত বকতে থাকি ‘ইয়াসমিন চল, তাড়াতাড়ি চল, আমি আইছি তরে নিতে, বাবার সাথে রাগ কইরা আইসা পড়ছস, ঠিক আছে, এখন চল যাই বাসাত।’ কে শোনে আমার প্রলাপ! দূর থেকে দেখি উঠোনের রোদে একটি অচেনা শাড়ি পরে বসে আছে ইয়াসিমিন, মাথা মুখ আড়াল করে রেখেছে শাড়ির আঁচলে। হু হু করে ওঠে বুক। যেন বুকের ভেতরে যা ছিল এতদিন, কোনও এক হায়েনা এসে সব কামড়ে খেয়ে গেল। আমাকে থামায় হাসিনা আর জামান, বলে ‘বিয়ে যখন হয়েই গেছে..’ বিয়ে আবার কি! ওকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি, আমার সঙ্গে যাবে ও। হাসিনা গিয়ে আমি যে যেতে বলছি ইয়াসমিনকে আমার সঙ্গে তা জানালে ইয়াসমিন বলে দিল ও যাবে না। চোখের সামনে আমার হারিয়ে যাওয়া বোন, আর আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে খালি হাতে, খালি বুকে! আমার সয় না। ও আমার সামনেও আসবে না, আমাকে মুখও দেখাবে না, আমার সঙ্গে যাবেও না। যতক্ষণ শরীরে মনে একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, অনুরোধ করেছি, আদেশ করেছি আমার সঙ্গে যেতে, বিয়ে হয়েছে ঠিক আছে, মিলন তার বাড়িতে ফিরুক, ইয়াসমিন অবকাশে ফিরে আসুক। দুজনে লেখাপড়া করুক, তারপর ঘটা করে লোক জানিয়ে বিয়ে দেওয়া হবে দুজনের। না, মানবে না ও। ঠিক আছে, বাড়ি চল, লেখাপড়া শেষ করতে না চাও, সংসার করার সময় হয়নি যদিও, কোথায় থাকবে কি করবে তা অন্তত আমাদের বুঝতে দাও, চল বাড়ি চল, বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে। না মানবে না ও। ঠিক আছে কালই করা হবে। না, কিছুই ও শুনবে না, যাবে না কোথাও ও। মিলন ওর স্বামী, স্বামীর সঙ্গে থাকবে ও। ওর আত্মীয় স্বজন বাবা মা ভাই বোনের চেয়ে বড় ওর স্বামী। আমাকে কেঁদে ফিরে আসতে হয়। আমাকে ভাসতে হয় নিজের ব্রহ্মপুত্রে। ও ফিরিয়ে দিল আমাকে। পুরো জগত তখন টলছে আমার সামনে। স্বপ্ন বলতে আমার যা ছিল, ভেঙে পড়ে আকস্মিক এক তুমুল তুফানে। ইয়াসমিনকে নিয়ে আমি একটি জীবন তৈরি করেছিলাম, কবিতার গানের জীবন, সেই জীবনটি বড় নিঃস্ব হয়ে যায়। হঠাৎ এক ভূমিকম্পে গুঁড়িয়ে যায় আমাদের উচ্ছঅল উতল জীবন। সর্বস্বান্ত হয়ে ময়মনসিংহ শহরের বাসে উঠি। বাসের ভেঁপুতে, কালিতে, বিকট চিৎকারে, দীর্ঘশ্বাসে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরি। বাড়ি খাঁ খাঁ করে। এত একা এ বাড়িতে আমার লাগেনি কখনও। বাড়িতে বাবা আছেন, মা আছেন, দাদা আছেন, কিন্তু কেউ যেন নেই। যেন একটি প্রাণী অবশিষ্ট নেই অবকাশে। নিজের কান্নার শব্দ শুনি একা একা। বাবার পুরুষরোগ, মার ধর্মরোগ, দাদার মুমুরোগ থেকে আমি নিজেকে অনেক আগেই দূরে সরিয়ে নিয়েছিলাম। ঘনিষ্ঠতা ছিল এক ইয়াসমিনের সঙ্গেই। অবকাশে ও ছাড়া আমার আপন কেউ ছিল না। যে মেয়েটি ধীরে ধীরে কবি হয়ে উঠছিল, গায়িকা হয়ে উঠছিল, ধীরে ধীরে ওর বয়সী যে কোনও মেয়ের চেয়ে ও অনেক বেশি সুচারু সুন্দর হয়ে উঠছিল, যে মেয়েটির এমনই অসাধারণ প্রতিভা, সে এমন এক সাধারণ ছেলের সঙ্গে বাকি জীবনের জন্য জীবন জড়ালো, যে ছেলে গানের গ ও জানে না, কবিতার ক ও না! বিষাদ আমাকে আচ্ছ!্বদিত করে রাখে, আশঙ্কা আমার শিয়রের কাছ থেকে নড়ে না। যে মেয়েটি স্বাধীনতা কাকে বলে ধীরে ধীরে শিখে উঠেছে, আর শিখে, পরিণত হয়ে সে এখন নিজেই নিজেকে পরাধীনতার শেকলে জড়িয়েছে সাধ করে। কালো উঠোন শাদা করে জ্যোৎস্না নামে। আমি একা বসে থাকি সে উঠোনে। কেউ নেই পূর্ণিমার একটি গান গায়, কেউ নেই আমাকে বুবু বলে ডাকে আর। মা মিহি সূরে কাঁদেন। বাবা কপালের শিরা চেপে বসে থাকেন। অবকাশের শিরদাঁড়ায় বোবা একটি যন্ত্রণা স্থির হয়ে থাকে।
অনেক অনেক বছর পর ইয়াসমিন যখন স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করছে, বলেছে সেদিন ভোরবেলা আলমারি থেকে আমার একটি কালো শাড়ি পরে বেরিয়েছিল মনের দুঃখে। বাবার ওই নিষ্ঠুর চাবুক ওর নিজের ওপর ধিককার এত বেশি বাড়িয়ে তুলেছিল যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কলেজে গেছে, ক্লাস করেছে, ক্লাস শেষে প্রবীরদের বাড়িতে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে অবকাশে ফিরে গিয়েছিল, কালো ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে কিছুক্ষণ। ভেবেছে ঢুকে যাবে, কিন্তু আবারও অভিমান এসে ওকে আবৃত করেছে। রিক্সা নিয়ে তখন সোজা নানির বাড়িতে গেছে, রাতে ঘুমিয়েছে, অপেক্ষা করেছে অবকাশ থেকে কারও আসার, কেউ এসে ওকে নিয়ে যাবে বাড়িতে। কেউ আসেনি। ওর ইচ্ছে করেছিল ঢাকা যেতে, কিন্তু হাতে ঢাকা যাওয়ার টাকা ছিল না, কারও কাছ থেকে টাকা ধার চাইতেও ওর লজ্জা হয়েছে। রাত কাটিয়ে পরে কলেজে গেছে, ওখানে থেকে আবার গেছে অবকাশে। আবারও দাঁড়িয়ে থেকেছে কালো ফটকের কাছে। ঢুকবে। শেষ অবদি ঢোকেনি। কোথায় যাওয়া যায়! ভাবতে ভাবতে শেষে কলেজস্ট্রিটে জামান নামে ক্লাসের একটি ছেলে থাকে, গ্রামের ছেলে শহরের কলেজে পড়ে, ছোট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে, তার ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে। কি হয়েছে কী ঘটেছে কিছু কাউকে বলে না। কি করবে বুঝে পায় না। কোথায় যাবে বুঝে পায় না। বাড়িতে না ফিরতে হলে একটি জিনিসই করতে হবে ওর, বাবার নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ একটি কাজ করেই ও নিতে পারে সে হল বিয়ে। আত্মহত্যার কথা ভেবেছে, কিন্তু ভয় লাগে আত্মহত্যা করতে। তাছাড়া বিষ যোগাড় করাও ঝামেলা। সুতরাং ওই একটি উপায়ই আছে, মেয়ে মানুষ যখন, মেয়ে মানুষের বাবার বাড়ি ছাড়া আরও একটি যাওয়ার জায়গা থাকে, সে হল স্বামীর বাড়ি। কিন্তু কাকে বিয়ে করবে ও! কাকে প্রস্তাব দেবে বিয়ের! কাকে লজ্জার মাথা খেয়ে বলবে, আমাকে বিয়ে কর! যার কথাই মনে আসে ওর, ভয় হয় হয়ত ফিরিয়ে দেবে। হয়ত ওকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। তখনই অনেকদিনের ভুলে যাওয়া মিলনের কথা ভাবে ও। মিলনকে খুঁজতে বের হয় ইয়াসমিন। পায় রাত্তিরে। কোনও রাখ ঢাক না করেই বলল, আমি বিয়ে করব এবং আজই। বিয়ে করতে চাইলে এক্ষুনি কর। তা না হলে আর আমাকে পাবে না। মিলন হতভম্ব। মিলন বলে, বাড়ি থেকে নাকি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে! ইয়াসমিন পুরোনো কথায় ফিরতে চায়নি। সে রাতেই ওরা চলে গেছে শহর ছেড়ে জামানকে নিয়ে। জামান ফুলপুরে নিজের বাড়িতে দুজনের থাকার ব্যবস্থা করেছে। পরদিন ফুলপুরে বিয়ের মত ব্যপারটি ঘটাতে ভয় ছিল ইয়াসমিনের, যদি কেউ ওকে চিনে ফেলে যে ও ডাক্তার রজব আলীর মেয়ে! যদি খবর রটে যায়! জামান ওদের নিয়ে হালুয়াঘাটে গিয়েছে, ওখানে রেজিস্ট্রি আপিসে নিয়ে দুজনকে দিয়ে বিয়ের কাগজে সই করিয়ে নিয়ে এসেছে। এটিও সহজ ছিল না। মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে বলে মিলন আর জামানকে সন্দেহ করা হয়। সন্দেহ মোচন করার জন্য দারোগাকে ঘুস দিয়ে কাজ সারতে হয়েছে।
আমি বাড়ি ফিরে মাকে বার বার বলেছি, কেঁদে ভেসে বলেছি, ‘কেন তুমি সেই রাতে নানির বাসায় খুঁজতে গেলা না ওরে!’ মা নিজের অপরাধের জ্বালায় ছটফট করেছেন, পাগলের মত কেঁদে কেঁদে বলেছেন, ‘আমি যদি জানতাম! আমি তো জানি না যে ওর নানির বাসায় ও আছে।’
‘তুমি গিয়া যদি নিয়া আইতা, তাইলে তো হইত না এইসব কাণ্ড!’
অঝোর ধারায় ঝরে মার চোখের জল। ‘আমি যদি জানতাম.. ভাবছি ফিইরা আইব। রাগ কইমা গেলে ফিইরা আইব। আমার কোলটা খালি হইয়া গেল..’
ইয়াসমিনের জীবন সম্পূর্ণই পাল্টো গেছে, আর ও আগের ইয়াসমিন নেই, আর ও আগের মত এই অবকাশ জুড়ে হাঁটবে না, গান গাইবে না, গাইবে না ওর প্রিয় গানটি আর, আমরা এমনি এসে ভেসে যাই, আর ও আগের মত আবৃত্তি করবে না, আর ও এ বাড়ি থেকে কলেজে যাবে না, কলেজ থেকে এ বাড়িতে ফিরবে না, আর বিকেল হলেই আমার সঙ্গে রিক্সায় চড়ে শহর ঘুরে বেড়াবে না, ওর অফুরন্ত সম্ভাবনার আর স্বাধীনতার জীবনে ইতি টেনেছে ও। ইয়াসমিন অবকাশ ছেড়ে চলে গেছে, বিয়ে করেছে একই ক্লাসে পড়ছে এক ছেলেকে, যে ছেলে কোনও একটি বাক্য শুদ্ধ করে বলতে জানে না, এ খবরটি আর ইয়াসমিন মরে গেছে খবরের মধ্যে আমার মনে হয় না কোনও ফারাক আছে। যে আমার ছায়ার মত আমার পাশে থাকত, সে নেই, সে মরে গেছে। সবচেয়ে আপন কেউ সবচেয়ে কাছের কেউ সত্যিকার মরে গেলে যেমন কষ্ট হয় আমার ঠিক তেমন কষ্ট হতে থাকে। আচমকা আমার সব তছনছ হয়ে যায়। এত একা আমার জীবনে কখনও আমি বোধ করিনি। পুরো জগতটি আমার এত খালি খালি কোনওদিন লাগেনি। নিজের জন্য যত কষ্ট হয় তার চেয়ে সহস্রগুণ হয় ইয়াসমিনের জন্য। অবকাশ খাঁ খাঁ করে। পুরো শহর খাঁ খাঁ করে। আমি ছুটি নিয়ে চলে যাই ঢাকায়। মা দুঃখ বেদনা যা আছে ভেতরে নিয়ে ইয়াসমিনকে দেখতে যান মিলনদের বাড়িতে যখন ও ফিরে আসে। ইয়াসমিনের অমন হারিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে সৈয়দ শামসুল হক ময়মনসিংহে ছুটে আসেন। সার্কিট হাউজে একদিন থাকেন, ওখান থেকে ফোনে কথা বলেন ইয়াসমিনের সঙ্গে। ওকে ফিরতে বলেন আগের জীবনে, রাগ করে এত বড় সর্বনাশ যেন না ঘটায়। ও ফেরে না। আমারও আশা ছিল ফিরবে, এরকম তো হয় মানুষের জীবনে, রাগ করে বিয়ের মত কাণ্ড ঘটিয়ে দেখে যে ভুল করেছে, তখন ফেরে। কত কেউ ফেরে, ইয়াসমিন ফেরে না।
কলকাতা থেকে ফিরে অবকাশে একা বসে থাকি। কেউ নেই যার কাছে কোথায় গিয়েছি কি করেছি সব গল্প শোনাবার। কেউ নেই যাকে নিয়ে বসে কলকাতা থেকে আনা গানের আর আবৃত্তির ক্যাসেট গুলো শুনব। আমার সুটকেস পড়ে থাকে সুটকেসের মত, কেউ ঝাঁপিয়ে খোলে না, কেউ বলে না কি কি আনছ দেখি, আর পছন্দ হলে এইটা আমারে দেও ওইটা আমারে দেও আবদার করার। শান্তিদেব ঘোষের খালি গলায় আমি কান পেতে রই গানটি শুনতে শুনতে উদাস শুয়ে থাকি অবকাশের একলা বিছানায়। ইয়াসমিন যদি অবকাশে থাকত, সেই আগের মত থাকত, গানটি শুনে ও পাগল হয়ে যেত। সেই মন খারাপ করা বিকেলে ফোন করি মিলনের বাড়িতে, ফোনের ওপাশে ইয়াসমিনের গলা শুনে রিসিভারটি পেতে রাখি আমি কান পেতে রই গানটির কাছে। গানটি শেষ হলে নিঃশব্দে কান পেতে থাকি ওদিক থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসে কি না, ওদিকেও কান পেতে আছে কি না ও। আছে, কান পেতে আছে, ওদিক থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। এদিকে বুক ভেঙে যাওয়ার শব্দ। একটি হু হু করা সুর বুঝি সত্যিকার গানের শিল্পীকে না কাঁদিয়ে পারে!
বিয়ে যখন করেছেই, যখন ফেরানোই যাবে না, অবকাশের সবাই ইয়াসমিনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করল। এক আমি ছাড়া। ইয়াসমিনও হঠাৎ হঠাৎ অবকাশে আসে পাজামা পাঞ্জাবি পরা মিলনকে নিয়ে। অতিথির মত আধঘন্টা একঘন্টা থেকে চা বিস্কুট খেয়ে ফিরে যায় শ্বশুর বাড়িতে। ও এলে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকি। বাবা যেদিন দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস ফেলে মার ক্রমাগত অনুনয়ের পর মেনে নিলেন বিয়েটি এবং ইয়াসমিনকে লাল বেনারসি আর সোনার গয়না গাটি কিনে দিয়ে মিলনের কিছু আত্মীয় স্বজনকে খাইয়ে বিয়ের ঘরোয়া অনুষ্ঠানটি করে দিলেন অবকাশ থেকে, সেদিনও আমার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। এই ইয়াসমিন অন্য ইয়াসমিন, আমি পারিনি ওর সামনে সহজ হতে, ও নিজেও পারেনি। ও এখন যে কোনও গৃহবধু, ও এখন বিয়ে হয়ে যাওয়া যে কোনও মেয়ে। খবর পাই শ্বশুর বাড়ির কড়া নিয়ম কানুনের মধ্যে আছে ও। শাশুড়ি, ভাসুর, ভাসুর বউ, স্বামী, স্বামীর আরও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ও নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছে। ওদের সুখ দুঃখই এখন ওর সুখ দুঃখ। ওরাই এখন সবচেয়ে ওর কাছের মানুষ। বাইশ বছর যার সঙ্গে কাটালো তার চেয়ে বেশি আপন এখন বাইশ দিনের পরিচিত মানুষ। ও এখন বিয়ে হয়ে যাওয়া যে কোনও মেয়ে। শ্বশুর বাড়ির মুরব্বিদের দেখলে মাথায় আঁচল তুলে দেওয়া মেয়ে। তাদের আদেশ নির্দেশ নতমস্তকে পালন করা মেয়ে। ও এখন শ্বশুরবাড়ির বয়সে বড়দের পায়ে পায়ে কদমবুসি করা মেয়ে। ও এখন রান্নাঘরে বসে শাশুড়ির কাছ থেকে কি করে রান্না করতে হয় শিখছে, কি করে স্বামীর পাতে মাছ মাংস দিতে হয় শিখছে, কি করে ঘরে বসে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে হয় শিখছে, কি করে মাথায় ঘোমটা টেনে ভাসুরের সামনে নত মুখে দাঁড়াতে হয় শিখছে, কি করে শ্বশুর বাড়ির সবার সঙ্গে নরম সূরে, নরম স্বরে কথা বলতে হয় শিখছে। কি করে ঘর গুছোতে হয়, কি করে কিছু আসবাবপত্র আর হাঁড়িপাতিলের স্বপ্ন দেখতে হয় শিখছে। কি করে নিজের স্বপ্নগুলো ভুলে যেতে হয় শিখছে। কি করে গান ভুলতে হয় শিখছে, কবিতা ভুলে যেতে হয় শিখছে। কি করে নিজের জীবনের সব সুরগুলো ভুলে যেতে হয় শিখছে।
০৮. বাহিরে অন্তরে
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরের প্যাকেটগুলো নিয়ে গেল নাইম। খবরের কাগজএর পরিবেশকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে বই, ওরা বই বিক্রি করার দায়িত্ব নিয়েছে। ঘাড় থেকে মস্ত বোঝা নামার মত বইগুলো নেমে যায় নাইমের হাতে। বই নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে বেশ সুন্দর ছাপা যায়, গুণে মানে বই ফাসকেলাস হতে পারে, কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটর নেই তো মরেছো। এই ব্যপারটি আমার হাড়ে হাড়ে বোঝা হয়েছে। ছুট্টি দিয়ে দিই ছুট্টি, বই ছাপার কম্মটি আমি আর নিজে করছি না। মনে মনে জুৎসুই একটি নাকে খতও হয়ে যায়। বইটি, পরে শুনেছি, মেলায় বিক্রি হয়েছিল, মেলায় সময়মত এলে হয়ত আরও বিক্রি হত। শেষদিকে আমলা কবি মোহাম্মদ সাদিক মন্ত্রণালয়ের গোপন একটি খবর জানালো আমাকে , বইটি নাকি নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা চলছে ওপর মহলে। অভিযোগ নিয়তি নামের কবিতাটি অশ্লীল। বইটির সবগুলো কবিতাই রুদ্রর সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙছে ভাঙছে সময়ে। নিয়তি কবিতাটিও রুদ্রর এক সময়ের আচরণ নিয়ে।
প্রতিরাতে আমার বিছানায় এসে শোয় এক নপুংশক পুরুষ
চোখে
ঠোঁটে
চিবুকে
উন্মাতাল চুমু খেতে খেতে
দুহাতে মুঠো করে ধরে স্তন।
মুখে পোরে, চোষে।
তষ্ণায় আমার রোমকূপ জেগে ওঠে
এক সমুদ্র জল চায়, কাতরায়।
চুলের অরণ্যে তার অস্থির আঙুল
আঙুলের দাহ
আমাকে আমূল অঙ্গার করে লোফালুফি খেলে
আমার আধেক শরীর তখন
সেই পুরুষের গা গতর ভেঙে চুরে
এক নদী জল চায়, কাতরায়।
শিয়রে পৌষের পূর্ণিমা
রাত জেগে বসে থাকে, তার কোলে মাথা রেখে
আমাকে উত্তপ্ত করে,
আমাকে আগুন করে
নপুংশক বেঘোরে ঘুমোয়।
আমার পুরোটা শরীর তখন তীব্র তৃষ্ণায়
ঘুমন্ত পুরুষটির স্থবির শরীর ছুঁয়ে
এক ফোঁটা জল চায়, কাঁদে।
কবিতাটি রোববার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, তখন সেই রোববার পত্রিকাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, বই নিষিদ্ধ হওয়ার কথা কেন ওঠে! কোন জিনিসটি অশ্লীলতা এবং কোনটি নয় তা বিচারের ভার কার ওপর! আমার তো কবিতাটিকে মোটেও অশ্লীল মনে হয়নি। শাহরিয়ার বলে, তোমার ওই মুখে পোরে, চোষে লাইনটি বাদ দিয়ে দাও। কেন বাদ দেব! কারণ মুখে পোরে চোষে ব্যপারটি অশ্লীল। হা! ছলে বলে কৌশলে যে শাহরিয়ার আমার স্তন মুখে পুরতে, চুষতে, চেয়েছিল, সে আমাকে শ্লীলতা শেখাচ্ছে! কোনও কারণ আমি খুঁজে পাই না লাইনটি বাদ দেবার। তৃষ্ণায় রোমকূপ কাঁপার কারণটি বর্ণনা করতে হলে লাইনটির প্রয়োজন, এরকম মনে হয়েছে। আমার মনে হওয়া অনেক পুরুষ বন্ধুর পছন্দ হয় না, যদিও সে পুরুষেরা যে কোনও রমণীয় রমণীর স্তন মনে মনে মুঠো করে ধরে, মুখে পোরে, চোষে এবং তকেক তকেক থাকে মনে মনের ব্যপারটি কখন কার ওপর সত্যিকার ঘটিয়ে ফেলা যায়। মোজাম্মেল বাবুর কথাই বলি। রূপে গুণে ধনে মানে অনন্য। আমার চেয়ে বয়সে ছোট। আপা ডাকে। কয়েক বছর ধরে প্রেম করছে এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। কাল বাদে পরশু সেই মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে। সেই বাবুই এক রাতে আমাকে একা পেয়ে উষ্ণ শ্বাস ফেলছিল আমার সারা গায়ে। তাকে আমি আমার নাগাল পেতে দিইনি।
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরের দুধরাজ কবি নিয়েও কথা হয়। দুধরাজ কবিটি হচ্ছে রুদ্র, কানাকানি চলে। যাকে উদ্দেশ্য করেই লিখি না কেন, কবিতা কেমন হল, আদৌ হল কী হল না, সেটিই বড়। শব্দের আড়ালে মানুষ ক্রমশ ম্লান হয়ে আসে। এ কবিতা কি আমি রুদ্রকে উদ্দেশ্য করে লিখেছি! যাকে উদ্দেশ্য করেই লিখি না কেন, এটি কবিতা। কবিতার পেছনে কে লুকিয়ে আছে, এটি আমার কাছে আর গবেষণার বিষয় নয়।
তার চে কুকুর পোষা ভাল
ধূর্ত যে শেয়াল, সেও পোষ মানে,
দুধ কলা দিয়ে আদরে আহলাদে এক কবিকে পুষেছি এতকাল,
আমাকে ছোবল মেরে
দেখ সেই কবি আজ কিভাবে পালায়।
এই কবিতার শোধ নিতে গিয়ে রুদ্র নিজে একটি কবিতা লেখে।
তুমি বরং কুকুর পোষো,
প্রভু ভক্ত খুনসুটিতে কাটবে তোমার নিবিড় সময়।
তোর জন্য বিড়ালই ঠিক,
বরং তুমি বিড়াল পোষো
খাঁটি জিনিস চিনতে তোমার ভুল হয়ে যায়,
খুঁজে এবার পেয়েছো ঠিক দিক ঠিকানা।
লক্ষ্মী সোনা, এখন তুমি বিড়াল এবং কুকুর পোষো।
শুকরগুলো তোমার সাথে খাপ খেয়ে যায়,
কাদা ঘাটায় দক্ষতা বেশ সমান সমান।
ঘাটাঘাটির ঘনঘটায় তোমাকে খুব তৃপ্ত দেখি,
অুমি বরং ওই পুকুরেই নাইতে নামো,
ঊংক পাবে, জলও পাবে।
চুল ভেজারও তেমন কোনো আশঙ্কা নেই,
ইচ্ছে মত যেমন খুশি নাইতে পারো।
ঘোলা পানির আড়াল পেলে
কে আর পাবে তোমার দেখা!
মাছ শিকারেও নামতে পারো
তুমি বরং ঘোলা পানির মাছ শিকারে
দেখাও তোমার গভীর মেধা।
তুমি তোমার স্বভাব গাছে দাঁড়িয়ে পড়ো,
নিলিঝিলির স্বপ্ন নিয়ে আর কত কাল?
শুধু শুধুই মগজে এক মোহন ব্যাধি
তুমি বরং কুকুর পোষো, বিড়াল পোষো।
কুকুর খুবই প্রভুভক্ত এবং বিড়াল আদরপ্রিয়,
তোমার জন্য এমন সামঞ্জস্য তুমি কোথায় পাবে?
রুদ্রর এই কবিতা পড়ে আমার মন খারাপ হয়। হয় কিন্তু তারপরও আমার জানতে ইচ্ছে হয় রুদ্র কেমন আছে, কি করছে, ভাল আছে তো! এই ইচ্ছেটি যখনই ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় যাই, অন্তত একবার হলেও অসীম সাহার ইত্যাদিতে আমাকে নিয়ে যায়। ওখানে নির্মলেন্দু গুণ আর অসীম সাহার সঙ্গে আমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখে। মোংলা থেকে এখনও ফেরেনি অথবা শিমুলকে নিয়ে ব্যস্ত এরকম খবর জোটে। পায়ের অসুখ সেরেছে কি? হাঁটতে পারছে? হাঁটে তবে থেমে থেমে। শুনি আমি, কোনও ক, খ, গ, ঘর পায়ের খবর শোনার মত শুনি। ভেতরে প্রাণ ফেটে যায় জানতে আরও কিছু, আরও অনেক কিছু। রুদ্র কি আমার কথা ভাবে, কিছু বলে! এসব এখন আর জিজ্ঞেস করা মানায় না। দীর্ঘ শ্বাস ফেলাও মানায় না, দীর্ঘ একটি শ্বাস তাই গোপন করি। বিয়ে ভেঙে গেলে অনেকে পরস্পরের শত্রু হয়ে যায়। আমি রুদ্রর শত্রু হব বা রুদ্র শত্রু হবে আমার, এমন আমি কখনও কল্পনাও করি না। এমন কি যে বন্ধুরা আমি বিয়ে ভাঙা একলা মেয়ে বলে অন্ধকার সুযোগ খুঁজেছে আমার শরীরের দিকে শরীর বাড়াতে, তাদের আমি নিজগুণে ক্ষমা করে দিই, বন্ধুত্ব নষ্ট করে দেওয়ার কথা ভাবি না।
খবরের কাগজে নাইম নির্বাসিত বাহিরে অন্তরের কিছু বিজ্ঞাপন ছেপে দেয়। একদিন বলে পরিবেশকরা খবর দিচ্ছে, বই বিক্রি হচ্ছে ভাল। এটুকু শুনেই আমি খুশি। নাইমের উদারতা আমাকে এমন বিনয়ী করে তোলে যে বই বিক্রির টাকার কথা তাকে আমি জিজ্ঞেস করি না। নাইমের আরও একটি উদারতা আমাকে চমকিত করে, কলকাতা যাওয়ার আগে তাকে আমি বলিনি যে আমি মিলনের সঙ্গে যাচ্ছি, কিন্তু সে যখন জানতে পারে যে আমি একা যাইনি, মোটেও সে এ নিয়ে তামাশা করেনি।
কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর বইমেলায় আমাকে পেয়ে শাহরিয়ার বেশ ভালমানুষের মত প্রশ্ন করেছে, ‘কেমন কাটালে ভারতে?’
আমিও ভালমানুষের মত উত্তর দিয়েছি, ‘ভালই।’
‘কোথায় কোথায় গেলে?’
‘গিয়েছি অনেক জায়গায়। অতসীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। চমৎকার মেয়ে অতসী।’
এরপরই ভালমানুষের মত আরেকটি প্রশ্ন, ‘এসটর হোটেলে মিলনের সঙ্গে রাতগুলো ভাল কেটেছে তো!’
খানিকটা চমকাই। খবর তাহলে জানা হয়ে গেছে শাহরিয়ারের। খবরটি যে অতসীর কাছ থেকে পেয়েছে, তা বুঝি। কলকাতা যাচ্ছি শুনে শাহরিয়ারই আমাকে অতসীর ঠিকানা দিয়েছিল, বলেছিল যেন দেখা করে বলি যে আমি শাহরিয়ারের বন্ধু। দেখা করেছিলাম, খুব ভাল সময় কেটেছিল অতসীর সঙ্গে, অতসী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তো বটেই, বাড়ির আর সবার সঙ্গেও চমৎকার একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমার। আমি একা যাইনি, আমার সঙ্গে মিলন গিয়েছে, এ খবরটি শাহরিয়ার অন্য রকম করে বলতে পারতো, কিন্তু তা না করে বোলতার মত এসে হুল ফুটিয়ে দিল। শাহরিয়ার এমনই। নির্বিকার হুল ফুটিয়ে যায়। অথচ নাইম কিন্তু হুল ফোটায় নি, যে কোনও সাধারণ খবর দেওয়ার মত বলেছে যে আমি কলকাতা যাওয়ার পর সে মিলনের বাড়িতে গেছে, মিলনের বউ জানিয়েছে যে মিলন কলকাতা গেছে, তখনই সে ধরে নিয়েছে মিলন আর আমি একসঙ্গে গিয়েছি। দুজন না গিয়ে আমি তো একাও যেতে পারতাম! পারতাম না কি! পারতাম। ভারতের যেখানে যেখানে ঘুরেছি, অনায়াসে সে জায়গাগুলোয় একা ঘোরা যেত। তবে একা ঘুরলে হয়ত ভাল লাগত না। অনেককিছু একা করতে ইচ্ছে হয় না। কোথাও যেতে হলে সঙ্গে একজনকে নেওয়া চাইএর অভ্যেস আমার অনেকদিনের। ইয়াসমিন মাঝে মাঝে রাগ হয়ে বলত, ‘তোমার বান্ধবীর বাসায় যাইতাছ, একলা যাও, সব সময় আমারে নিয়া যাইতে হইব কেন!’ অথবা রুদ্র ময়মনসিংহে এলে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেও ইয়াসমিনকে নিয়ে যেতাম। ইয়াসমিন হাতের কাছে না থাকলে সুহৃদকে। রুদ্র অনেকদিন রাগ করে বলেছে, তুমি একা আসতে পারো না! নিশ্চয়ই পারি, কেন পারবো না! একা কলেজে যাচ্ছি, কলেজ থেকে একা বাড়ি ফিরছি। সবই হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে কেউ একজন থাকলে ভাল লাগে। আপন কেউ থাকলে ভাল লাগে। সবে মাস পেরোলো কলকাতা থেকে ফিরেছি, হঠাৎ একদিন নাইমের আবদার, ‘চল কলকাতা যাই, সাত দিনের জন্য।’ কেন? কেন তা নাইম বলে না। কেন সে যাবে কলকাতা তা খুব করে যখন জানতে চাই, সে বলে পত্রিকার জন্য কিছু ব্যবসায়িক কাজ আছে তার, তাই সে যাচ্ছে। সে তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আমার যদি কলকাতায় ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হয়, আমি অনায়াসে তা করতে পারি। এমনিতে নাচুনে বুড়ি, তার ওপর ঢোলের বাড়ি। নাইমের প্রস্তাবে আমার রাজি হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল, ময়মনসিংহের বাড়ি আমার কাছে বড় দুর্বিষহ হয়ে উঠৈছিল। সুহৃদ নেই, ইয়াসমিন নেই। বাড়িটিতে যতক্ষণ থাকি মরার মত শুয়ে থাকি। এক অসহ্য নিঃসঙ্গতা আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল, তার পরও যদি ডাক্তারির চাকরিতে সামান্য স্বস্তি থাকত, ওখানেও অলস অবসর জুড়ে রাজ্যির ভাল না লাগা আমাকে ঘিরে ধরে। কলকাতা রওনা হই। তবে যাবার আগে মোটেও ভুলি না সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্য গরুর মাংস নিতে। তিনি গরুর মাংস খেতে চেয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলাম এর পর কখনও এলে নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।
কলকাতা পৌঁছে পশ্চিম বঙ্গের তথ্য কেন্দ্রে গিয়ে প্রথমেই সৌমিত্র মিত্রর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দিকে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের একটি সরকারি গেস্ট হাউজে দুজনের জন্য দুটি ঘরের ব্যবস্থা করে গাট্টিবোঁচকা যার যার ঘরে রেখে ছোটা শুরু হল নাইমের, সঙ্গে আমি। সিদ্ধার্থ সিংহ নামের একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে ছোটে। সিদ্ধার্থ সৌমিত্র মিত্রর আবৃত্তিলোকের সদস্য, সৌমিত্র মিত্রর খাঁটি শিষ্য, সিদ্ধার্থ নিজেও আবৃত্তি করে। সিদ্ধার্থর সঙ্গে নাইমের আলাদা একটি সম্পর্কও আছে, নাইমের খবরের কাগজ পত্রিকাটির সে কলকাতা প্রতিনিধি। লেখকদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে লেখা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো তাঁর দায়িত্ব। কলকাতায় আপাতত সে পথ প্রদর্শক। প্রথমেই মাংস নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি সত্যি সত্যি আমি বাংলাদেশ থেকে গরুর মাংস এনেছি। কোরবানি-ঈদের মাংস। মাংস পেয়ে তিনি বেজায় খুশি, ‘গীতা ও গীতা দেখে যাও, কী এনেছো ও।’ মাংস নিয়ে সারা বাড়ি দৌড়োচ্ছেন তিনি। সেদিনই তিনি তাঁর স্ত্রী গীতাকে বলে বলে অস্থির করে মাংস রান্না করিয়ে ছাড়লেন। প্রথম যখন এসেছিলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে, তখন মহা উৎসাহে নিজে রেঁধে আমাকে বাটিচচ্চড়ি খাইয়েছিলেন, কলকাতা চিনিয়ে চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন গ্র্যান্ড হোটেলের আনন্দ পুরস্কার অনুষ্ঠানে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় পেয়েছিলেন পুরস্কার। আমি কলকাতা থেকে দিল্লি আগ্রা কাশ্মীর যাবো শুনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মোটেও খুশি হননি, জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘ওখানে কী দেখবে? তার চেয়ে আমার সঙ্গে চল। আমরা টেংরা যাবো, বজবজ যাবো।’
টেংরা আর বজবজের নাম শুনে আমি অবাক। জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওখানে কী আছে দেখার?’
সুভাষ মুখোপাধ্যায় হেসে বললেন, ‘মানুষ।’ তখন হৈ চৈ করা, বাড়ির সকলের সঙ্গে শিশুতোষ দুষ্টুমিতে মেতে থাকা, সামান্য বাটি চচ্চড়ি আর এক গেলাস রামের জন্য তুমুল হল্লা করা মানুষটিকে আমি সত্যিকার চিনতে পারি। তাঁর দৈনন্দিন দোষ জমে জমে যত উঁচুই হোক না কেন, তাঁকে আড়াল করার সাধ্য কারওরই নেই। সব ভেঙে সব ফুঁড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন বেরিয়ে আসেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নাইম আমাকে বিষম এক চমক দেয়। আমাকে সে নিয়ে যায় ছ নম্বর প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে আনন্দবাজার আর দেশ পত্রিকার আপিসে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শংকরলাল ভট্টাচার্যর কাছে নাইম তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য কলাম চাইতে গেল। ফাঁকে আমারও দেখা হল কথা হল নামি দামি লেখকদের সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ দেবালয়ে গিয়ে দেবতাদের দেখে এলাম। লেখা পড়ে যাঁকে চিনি, যাঁকে কল্পনায় সাজিয়ে নিই একরকম করে, দেখা হলে সেই কল্পনার মানুষটির সঙ্গে আসল মানুষটিকে মেলানো যায় না কিন্তু ছোটখাটো ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেওয়া যায় সহজে, শীর্ষেন্দুর কালো স্যান্ডেলের সঙ্গে উৎকট নীল রঙের মোজাটি ক্ষমা করে দিই। মন দিয়ে তাঁর ময়মনসিংহের স্মৃতিচারণ শুনি। ঢাকায় বসে প্রতি সপ্তাহে দেশ পত্রিকাটি আদ্যেপান্ত পড়ি। এই একটি সাহিত্য পত্রিকা যা আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যের দ্য বেস্ট সাহিত্য পত্রিকা। আর আমি আজ সেই ঘরে বসে আছি, যেখান থেকে দেশ বেরোয়, তাঁদের সামনে বসে আছি যাঁরা দেশ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন, দেশে লেখেন এবং তাঁদের সামনে বসে আছি সেই শৈশব থেকে যাঁদের লেখা বই আমি গোগ্রাসে পড়ি, বিশ্বাস হয় না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে কাগজপত্রের স্তূপ। তিনি তাঁর ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এমন হাসির গল্প লেখেন, অথচ মানুষটি কিন্তু আদপেই হাসেন না। তাঁকেও নাইম অবলীলায় আবদার করল তার কাগজের জন্য কলাম লেখার। এমন হয়েছে, যে লেখক বা যে কবিকেই নাইম সামনে পায়, কলাম লেখার আবদার করে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্র্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঢাকায়, আবার দেখা হল কলকাতায়। তাঁর ঘরেই বসেন গৌরকিশোর ঘোষ, মুগ্ধ হয়ে যাই তাঁর ব্যবহারে, যেন আমাদের সেই কতকাল থেকে চেনেন তিনি। একটি জিনিস লক্ষ করছি, পূর্ব বাংলায় যাঁদের জন্ম, যাঁরা দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে এসেছেন, তাঁরা পূর্ব বাংলার মানুষ দেখলে বড় আপন মনে করেন, ফেলে আসা জীবনটির দিকে ফিরে তাকান। বলেন কেমন ছিল তাঁর বাড়িটি, বাড়ির পাশের বাগানটি, তাঁর গ্রাম বা শহরটি। জানতে চান ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনা এখন দেখতে কেমন। শংকরলাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে সানন্দা আপিসে দেখা হল, তিনি আমাদের ছাদে নিয়ে বসিয়ে ইদানীং তিনি কি নিয়ে ভাবছেন কি লিখছেন কি পড়ছেন ইত্যাদি অনেক কথা বললেন। সবখানেই আমি শ্রোতা। এর বেশি কিছু হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
সৌমিত্র মিত্র অনেক জায়গায় নিয়ে গেলেন আমাদের। আবৃত্তিশিল্পী দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে নিলেন, তাঁর বাড়িতে দুপুরের খাওয়া হল অনেক রকম মাছ দিয়ে। নাইম দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের কাছেও লেখা চেয়েছে। পারলে সে জ্যোতি বসুর কাছে যায় লেখা চাইতে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেও নিয়ে গেলেন সৌমিত্র। বৈঠক ঘরে শক্তি বসেছিলেন খালি গায়ে। সেই খালি গায়ের শক্তি আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলেন। আমাদের খাওয়ালেন। আমাকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আগেই চেনেন, স্ত্রী পুত্র নিয়ে অবকাশে তিনি বেড়াতে গিয়েছেন। শক্তি তাঁর বাড়িটির দোতলায় একটি ছোট ঘর দেখিয়ে বললেন, এর পর এলে আমি যেন ও ঘরটিতে থাকি, ও ঘরটি তিনি আড্ডার জন্য বানাচ্ছেন। উদাসীন হিসেবে শক্তির নাম আছে, কবিতাই তিনি কোথায় লিখে রাখেন খোঁজ পান না আর নাইম কিনা শক্তিকে আবদার করল তাঁর পত্রিকায় কলাম লিখতে! অবশ্য শক্তি সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেলেন। পরের সপ্তাহেই তিনি লিখে রাখবেন কথা দিলেন।
আরও একটি চমক নাইম আমাকে দিল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে রাতের খাবারের নেমন্তন্নে নিয়ে গিয়ে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঢাকায় দুবার আমার দেখা হয়েছিল। প্রথমবার স্বরশ্রুতির আবৃত্তি উৎসবে। উৎসবের তিনি বিশেষ অতিথি ছিলেন। মোজাম্মেল বাবু, শাহরিয়ার, ইমদাদুল হক মিলন এবং আরও কজনের সঙ্গে আমি যখন ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাঠে আড্ডা দিচ্ছিল!ম, দেখেছি তিনি কাছেই বসে আছেন ভক্তপরিবেষ্টিত। অটোগ্রাফ দিচ্ছেন তরুণ তরুণীদের বাড়িয়ে দেওয়া কাগজে, খাতায়, বইয়ে। আমাদের আড্ডায় হঠাৎ মোজাম্মেল বাবু বলল, ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো সবাইকে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন, কেমন হয় আমরা যদি তাঁকে এখন অটোগ্রাফ দিই।’ প্রস্তাবটি মজার, সবাই আমরা হেসে উঠি কিন্তু কার স্পর্ধা আছে সুনীলকে অটোগ্রাফ দেবার! বাবু আমাকে বলে, ‘চলেন আপা সুনীলদাকে অটোগ্রাফ দিয়ে আসি।’ কারও কানের কাছে বেলুন ফাটিয়ে মজা করে মজা দেখার উৎসাহ নিয়ে আমি উঠি। দুজন আমরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ালাম, তিনি ভাবছিলেন আমরা অটোগ্রাফ নিতে এসেছি, প্রায় হাত বাড়াচ্ছিলেন আমাদের হাতে কোনও খাতা বা বই থাকলে তা নিতে, এমন সময় বাবু বলল, ‘সুনীলদা, আমরা আপনাকে অটোগ্রাফ দিতে এসেছি।’ শুনে আমি যদিও মুখ আড়াল করতে চাচ্ছি লজ্জায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু মোটেও বিব্রত হননি, বিস্মিত হননি বরং বিনীত হেসে বলেছেন, ‘আমার কাছে যে কাগজ নেই।’ কাগজ সংগ্রহ করা হল এবং সেই কাগজে আমরা দুজন দুটো অটোগ্রাফ দিলাম আর সেই ছেঁড়া কাগজটি বাংলার বিখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক তাঁর শার্টের বুক পকেটে বেশ যত্ন করে রেখে দিলেন। অটোগ্রাফ দিয়ে আমাদের আড্ডাটিতে ফিরে এলে সকলে ঘিরে ধরল, উৎসুক জানতে কী ঘটেছে। এর পরের দেখাটির সময় খুব সামান্যই কথা হয় দুজনের। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের, বুঝি যে মনে নেই আমি যে তাঁকে অটোগ্রাফ দিয়েছিলাম। আমি আমার সেই স্পর্ধার কথা আর মুখ ফুটে বলি না। কলকাতায় তাঁর ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনের বাড়িতে বিস্তর পানাহারের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী স্বাতী মিষ্টভাষী সুন্দরী। সৌমিত্র মিত্র তাঁর স্ত্রী মুনমুনকে নিয়ে এসেছিলেন। মুনমুনও বেশ সুন্দরী। খুব অনায়াসে স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় আর মুনমুন মিত্র মদ্যপান করলেন। এর আগে আমি কোনওদিন কোনও মেয়েকে মদ্যপান করতে দেখিনি। পান করার ক্ষমতা আমার কোমলে সীমিত বলে একটি লিমকার গ্লাস নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু সকলের ষড়যন্ত্রে দেখি আমার গ্লাসে দুফোঁটা ঝাঁঝালো গন্ধের উপদ্রপ। কয়েক চুমুকের পর আমার মাথা ঘুরে ওঠে। কিন্তু ঘুরে ওঠা মাথায় ভাল লাগার এক রিমিঝিমি শব্দ শুনি যখন গান গাইতে শুরু করলেন সবাই। যে যা পারে গাইছেন, হেঁড়ে গলায়, ধরা গলায় আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একের পর এক গেয়ে যাচ্ছেন যেন পুরো গীতবিতানই তিনি সে রাতে গেয়ে শেষ করবেন। রাত গড়াতে গড়াতে মধ্যরাতে ঠেকলো। মিলন আমাকে যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিয়ে আসতে সংকোচ বোধ করেছে, সেখানে নাইম আমাকে নিয়ে এসে গৌরব বোধ করেছে। কাছ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত বিশাল মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হল, বন্ধুর মত আড্ডা হল। ভাল লাগা আমাকে বড় নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে রাখে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ এরকম বড় কবিদের সঙ্গে দুদিন পর আমার কবিতা পড়ারও আমন্ত্রণ জোটে। সৌমিত্র মিত্রের আবৃত্তিলোক আয়োজিত জুঁই ফুলে সাজানো শিশির মঞ্চে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং আরও আরও কবিদের সঙ্গে এক মঞ্চে সভয়ে সলাজে একটি কবিতা পড়ি। ধন্য হই কি? ধন্য হই। আকাশ ছোঁয়া কিছু কিছু স্বপ্ন থাকে মানুষের আমার স্বপ্ন এতদূর পর্যন্ত পৌঁছোতে কখনও সাহস করেনি।
সিদ্ধার্থ আমাকে বলেছে যে নাইম তাকে আমার কিছু বই পাঠিয়েছে, বইগুলো সে কলেজ স্ট্রিটের প্যাপিরাস বুকস নামের দোকানে রেখেছে। দেশ এ ছোট একটি বিজ্ঞাপন দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছে। প্যাপিরাসে কিছু বিক্রি হল কী না তা আমি নাইম বা সিদ্ধার্থর কাছে কিছু জানতে চাই না। জানতে চাই না লজ্জায়, যদি শুনতে হয় একটি বইও বিক্রি হয়নি। বইটি নিয়ে আমার লজ্জার শেষ নেই, হেলাল হাফিজ বলেছিলেন আমার নাকি অহংকারও আছে। বইটি যখন ছাপা হচ্ছে প্রেসে, হেলাল হাফিজ তাঁর বইয়ের প্রকাশক অনিন্দ্য প্রকাশনীর নাজমুল হককে অনুরোধ করেছিলেন আমার বইটির দায়িত্ব নিতে। প্রচ্ছদশিল্পী খালিদ আহসানও অনুরোধ করেছিলেন নাজমুল হককে। আমি ছিলাম সামনে। নাজমুল হক প্রথম ইতস্তত করছিলেন। পরে অবশ্য নিমরাজি জাতীয় কিছু হলেও আমি সকলকে অবাক করে দিয়ে বলেছিলাম বইটি আমি অনিন্দ্যকে দেব না, আমি নিজেই ছাপবো। নাজমুল হক চলে গেলে হেলাল হাফিজ আমাকে বলেছিলাম, আমার ওই অহংকারটুকু তাঁর খুব ভাল লেগেছে। যে লোক দ্বিধা করছে বইটি ছাপতে, তাকে আমি কেন দেব বই! এইটুকু অহংকার বা আত্মসম্মানবোধ যদি না থাকে মানুষের, তবে থাকে কী!
নাইমের সাহস দেখে মাঝে মাঝে আমি খুব বিস্মিত হই। বড় বড় লেখক কবিদের কাছে তার নতুন পত্রিকাটির জন্য খুব য়চ্ছন্দে কলাম চাইছে সে। এমনকী পুর্ণেন্দু পষনীর বাড়িতেও সে গেছে লেখা চাইতে। আমার কখনও এই স্পর্ধা হত না জানি। পূর্ণেন্দু পষনীর কথোপকথন আর আমরা আবহমান ধ্বংস ও নির্মাণের সকল শব্দাবলী আমার তখন ঠোঁটস্থ। পূর্ণেন্দু পষনীকে যখন আমি দেখছি চোখের সামনে, মনে মনে আওড়াতে থাকি কোনও এক নন্দিনীর জন্য কোনও এক শুভংকর যে কথা বলেছিল, মানুষ, নন্দিনী/ শুধু মানুষ/ উত্তাল ঝড়ঝাপটায়/কেরোসিন কুপির শিউরে-কাঁপা শিখার নিচে/ দুঃখিত মানুষের মুখগুলো/ তাদের স্যাঁতসেঁতে চামড়ায় শস্য এবং ডিজেলের গন্ধ,/ তাদের ঘামের নুনে/অভ্রের ঝিলিক, তাদের হাতের চেটোয়/কোদাল কুড়োল এবং ইঞ্জিন চাকার ছাপ। এই সব মানুষের মুখের দিকে তাকালেই/ আমার দেখা হয়ে যায়/আকাশ, মেঘ, পর্বত চূড়ার পিছনে সূর্যোদয়/দেখা হয়ে যায় নতুন নতুন বৃক্ষের জন্ম/বৃক্ষকে ঘিরে/জ্বলজ্বলে জনপদের বিকাশ। পূর্ণেন্দী পষনীর কবিতা আমার পছন্দ বলে নাইম সৌমিত্র মিত্রকে ধরে পষনীর সঙ্গে আমার যেন দেখা হয়, তার ব্যবস্থা করেছে। কোথায় নাইম তার ব্যবসার কাজ করবে, তার কিছুই নয়। সে ব্যস্ত আমার অপ্রত্যাশিত কিছু চমৎকার ব্যপার ঘটিয়ে আমাকে খুশি করতে। লক্ষ্য করেছি আমার খুশি দেখলে নাইম খুশি হয়। কিসে আমার ভাল লাগবে, আমার আনন্দ হবে তা নিয়ে সে সারাক্ষণই ভাবছে। পারলে সে আকাশের চাঁদটিও আমার হাতে এনে দেয়। আমার কোনও বন্ধুকেই কখনও এমন নিবেদিত হতে দেখিনি। কেবল বন্ধুই কেন! যাকে আমি ভালবেসেছিলাম পাগলের মত, সেই রুদ্রই কি কোনওদিন ভেবেছে!
আমি মুগ্ধ নয়নে পূর্ণেন্দু পষনীকে দেখছি, কথা বলতে গেলে যদি ভুল কিছু বলে ফেলি, এই ভয়ে কথাই বলছি না কিন্তু, নাইম, দিব্যি, যেন পষনী তার খালাতো ভাই এমন গলগল করে তাও আবার কুমিল্লার উচ্চারণে লেখা চাইছে। যেন লেখা চাইছে কোনও সংববদপত্রের ছাপোষা কলামিস্টের কাছে। এত বড় বড় কবির সঙ্গে নাইমের কোনও ভেবে চিন্তে কথা বলতে হয় না। লেখা চাওয়া তার কাছে কি ভাই লেখাটা এহনও দিতাছেন না যে! যত তাড়াতাড়ি পারেন লেখাটা রেডি কইরা রাইখেন, কালকের মধ্যেই চাই এর মত সহজ। নাইম কারও লেখা পড়েনি, কাউকেই তার বিশাল কিছু মনে হয় না। নাইমের উচ্চাকাংখা প্রচণ্ড। নামী দামী সাহিত্যিককে দিয়ে লেখাতে পারলে তার পত্রিকা ভাল চলবে, সম্পাদক হিসেবে তার নাম হবে, এটিই তার কাছে বড়। কারও সময় আছে কী না কলাম লেখার, কেউ আদৌ কলাম লিখতে চান কী না বাংলাদেশের একটি নতুন কাগজে, তাও জানতে চায় না। সে টাকার কথা বলে, এও জানতে চায় না তার ওই কটি টাকার কারও প্রয়োজন আছে কী না। অবশ্য লিখেছেন অনেকে, সে পূর্ববাংলাকে ভালবাসেন বলেই লিখেছেন, আমার মনে হয় না অন্য কিছুর জন্য।
সৌমিত্র মিত্র একসঙ্গে ঠিক কতগুলো কাজ করেন, তা আমার পক্ষে ধারণা করা শক্ত। যতক্ষণই তাঁকে দেখেছি, তিনি কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত। আবৃত্তি করেন, ওদিকে আবার সরকারি তথ্য অফিসারের চাকরি করেন। কুমুদ মান্না নামের এক ব্যবসায়ী লোককে বলে আমাদের নৌকো চড়াবার ব্যবস্থা করলেন একদিন। রাতের গঙ্গা। গঙ্গা দেখার বড় শখ ছিল আমার। গঙ্গার জল ছলাৎ ছলাৎ করে শব্দ তুলে আমার পা ভিজিয়ে দেয়। আমি ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে গঙ্গার কোনও অমিল দেখতে পাই না। আমি যখন গঙ্গার বিভোর ছিলাম, নাইম গঙ্গার দিকে পেছন ফিরে তার ভাবনার গভীর জলে ডুবে ছিল কী করে আমাকে আরও বেশি বিহ্বল করা দেওয়া যায়, আমাকে আরও বিমুগ্ধ করা যায়!
হঠাৎ নাইম আমাকে এক সকালে বলল, ‘তাড়াতাড়ি রেডি হ। একজায়গায় যাইতে হইব।’কোন জায়গা তার কিছুই বলে না সে। তারপর ইস্টিশনে নিয়ে ট্রেনে ওঠালো, সৌমিত্র মিত্রও যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে, তিনি বললেন যে শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি আমরা। শান্তিনিকেতন! ঝিরঝির শান্তি ঝরতে থাকে হৃদয়ে। আমার আনন্দিত চোখদুটো নাইম দেখল। প্রতিদিনই নাইম আমাকে চমক দিচ্ছে। গোপনে যে সে আয়োজনটি করে রেখেছিল, তার কোনও আভাস পাইনি। শান্তিনিকেতনে পৌঁছে আমার জীবন সার্থক হয়। শান্তিনিকেতনে তখন মিষ্টভাষী মৃদুভাষী কবি শঙ্খ ঘোষ ছিলেন। প্রিয় লেখক, প্রিয় কবিদের সঙ্গে দেখা হলে কী কথা বলব ভাবতে ভাবতেই আমার সময় যায়। বেশির ভাগই বাকরুদ্ধ বসে থাকি। কী এক ঘোরের মধ্যে সারাদিন রবীন্দ্রনাথের বাড়িঘর, ছাতিমতলা, আম্রতলা সব ঘুরে ঘুরে দেখি। যে সব জায়গায় দর্শকের ঢোকা নিষেধ, শান্তিনিকেতনের উপাচার্যের কল্যাণে সে সব জায়গাতেও আমাদের ঢোকার অনুমতি মেলে। রবীন্দ্রনাথের চেয়ারে বসিয়ে নাইম আমার ছবি তুলতে চাইছিল, এত বড় স্পর্ধা আমার হয়নি সেই চেয়ারে বসার, আমি মেঝেয় বসি। সবকিছু আমার যেন কেমন স্বপ্নের মত লাগছিল, রাতে গেস্ট হাউজে ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশালতার কথা ভেবে আমার আবেগ উপচে পড়ে। কেঁদে ভাসাই। কোনও কল্পিত ঈশ্বরের পায়ে পড়ে লোকে যেমন কাঁদে, আমার কান্নাও তেমন। তবে এ ঈশ্বর বটে, কল্পিত নয়। না, আমি কোনও পাপ মোচনের অনুরোধ করে কাঁদি না। এ কান্না কোনও সুখের নয়, দুঃখের নয়। এ কান্না রবীন্দ্রনাথকে তীব্র করে অনুভব করার কান্না। আমার কান্নার কোনও কারণ নাইমের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। সে আমার পিঠে হাত রাখে, পিঠের হাতটি একটু একটু করে নিচের দিকে নামে। হাতটি আমার সন্দেহ হয় যে আমার প্যাণ্টের বোতামের দিকে নামতে চাইছিল। আমি দ্রুত সরিয়ে দিই নাইমের হাত। সম্ভবত সে ভেবেছে, আর সব পুরুষের মত, যে, যে মেয়ে কোনও পুরুষ নিয়ে অনেকদিনের জন্য হাওয়া হয়ে যায়, হোটেলে রাত কাটাতে দ্বিধা করে না, তার কাছে নিশ্চয়ই শারীরিক সম্পর্ক নিতান্তই ডালভাত। নাইমকে আমি ভেবেছিলাম সবার থেকে আলাদা। কিন্তু তার হাতটি আমার পিঠ থেকে নিচের দিকে নামছিল বলে ইচ্ছে না হলেও তাকে আমার তাদের কাতারেই ফেলতে হয় যারা মেয়েমানুষের শরীর দেখলে লোভ সংবরণ করতে পারে না। কিন্তু এরকম কি কোনও পুরুষ আছে হাতের কাছে কোনও রমণী পেয়েও কামগন্ধহীন রাত কাটাতে পারে! নেই হয়ত। নাইমের চরিত্রের অন্য দিকগুলো আমার ভাল লাগে বলে আমি ক্ষমা করে দিই তার ওই কুৎসিত হাতটিকে। তাকে একটুও বুঝতে দিই না যে আমি বুঝেছি তার হাত যে নামছিল, নাইমও এমন ভাব করে যে হাতটি সে পিঠেই কেবল রেখেছিল, মোটেও তার হাতটির গন্তব্য অন্য কোথাও ছিল না।
কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর নাইম আমাকে তার পত্রিকায় আমাকে কলাম লেখার আমন্ত্রণ জানায়। এ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি পত্রিকায় তা কবিতা আর গল্প। কোনওদিন কলাম বলে কোনওকিছু লিখিনি। আমি ‘ধুর কলাম কি করে লিখতে হয় আমি জানি না,’ বলে উড়িয়ে দিতে চাইলে সে বলে, ‘তোর যা ইচ্ছে করে তাই লেখ, ঘাবড়ানির কিছু নাই।’ ঘাবড়ানির কিছু নাই হয়ত, কিন্তু আমি ঘাবড়ে যাই। কলাম লেখার অভ্যেস অভিজ্ঞতা না থাকলে কি করে লিখব! নাইম জোর করে, ‘লিখতেই হবে। হক ভাই বইলা দিছে তোরে যেন কলাম লিখতে বলি।’ সৈয়দ হক আমাকে স্নেহ করেন জানি, নিজে তিনি আমার কবিতা পড়ে তাঁর বইয়ের প্রকাশক বিদ্যাপ্রকাশএর মালিক মজিবর রহমান খোকাকে বলেছেন আমার বই ছাপতে। একটি চিঠিও লিখে দিয়েছিলেন যেন সেই চিঠি আর আমার কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে খোকার সঙ্গে দেখা করি। করেছিলাম, খোকা বলেছেন, ‘আমরা তো নতুন কবির কবিতার বই ছাপি না। তবে আপনি যদি টাকা দেন, তাহলে ছাপতে পারি।’ রাগ করে চলে এসেছিলাম। টাকা দিয়ে যদি বই ছাপতে হয় তাহলে নিজেই ছাপতে পারি। খবরের কাগজ পত্রিকাটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি কাগজ। সাপ্তাহিক পত্রিকার যে চরিত্র বিচিত্রা তৈরি করেছিল, বিচিত্রার পথ অনুসরণ করে সন্ধানী আর রোববার বেরিয়েছে, কিন্তু সব চলতি ধরন ভেঙে নতুন চরিত্রে খবরের কাগজ দেখা দিয়েছে। নিউজপ্রিণ্টে ছাপা। পঈচ্ছত নিউজপ্রিণ্টে। দাম কম। যে কারও কেনার সামর্থ আছে। কোনও কবিতা গল্প নেই, সিনেমার খবর নেই। খবরের মধ্যে এক রাজনীতির খবর। বাকি লেখাগুলো কলাম, রাজনীতি সমাজ সাহিত্য নিয়ে বড় বড় লেখক বুদ্ধিজীবী আর রাজনীতিবিদদের কলাম। যে লেখকরা আগে কোনওদিন কলাম লেখেনি, এই প্রথম তারা খবরের কাগজের জন্য কলাম লেখা শুরু করেছে। এত জনপ্রিয় লেখকদের এক সঙ্গে এক পত্রিকায় জড়ো করা নতুন একটি ঘটনা বটে। পত্রিকা জগতে খবরের কাগজ একটি আন্দোলনের মত।
কিছু কিছু আমন্ত্রণ আছে আশার অতীত। খবরের কাগজে লেখার জন্য এই আমন্ত্রণটি আমি কখনই আশা করিনি। এমন একটি জনপ্রিয় কাগজে কিছু লেখার সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের ব্যপার। ভাগ্যের পেছনে মানুষ দৌড়োয়। ভাগ্য আমার দোরগোড়ায় এসে পড়ে থাকে। আমি তাকে মোটে ছুঁয়ে দেখি না। কিন্তু নাইমের উৎসাহ এবং তাগাদা আমাকে কাগজ কলম হাতে নিতে বাধ্য করে। কী লিখব কী লিখব ভাবতে ভাবতে হাত কচলাতে কচলাতে বাহুতে ঘসতে ঘসতে চিহ্নটি চোখে পড়ে। ডান বাহুতে সাদা একটি বৃত্ত, সিগারেটে ত্বক পোড়ার স্মৃতি। ঘটনাটি মনে পড়ে, অনেক বছর আগে একটি রাস্তার ছেলে আমার বাহুতে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরে হা হা করে হাসছিল আনন্দে। যখনই ওই দৃশ্যটি মনে পড়ে আমার, আমি সেই পোড়ার কষ্টটি অনুভব করি। সামনে কাগজ কলম, আর আমি সেই কষ্টটি অনুভব করছি। এই অনুভবটিই আমাকে লেখায় সেদিনের সেই ঘটনাটি। সিনেমা থেকে বেরিয়ে রিক্সায় চড়েছি, রিক্সা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে, তখনই অনুভব করি ডান বাহুতে তীব্র একটি যন্ত্রণা। ‘আধখাওয়া জ্বলন্ত একটি সিগারেট আমার বাহুতে চেপে ধরেছে বারো তেরো বছর বয়সের একটি ছেলে। .. ভাবছিলাম চিৎকার করব, কাউকে ডাকব, বিচার চাইব। কিন্তু কিছুই করিনি। কারণ, লোকেরা ভিড় করে আমাকে দেখবে, আমার যন্ত্রণা, আমার আর্তস্বর, আমার ক্রোধ আমার কান্না দেখবে। সবাই তারা আমাকে উপভোগ করবে। আমার ডান বাহুতে এখনও পোড়া দাগ, আমি সেই নির্যাতনের চিহ্ন এখনও বহন করে চলেছি। এ আমার সৌভাগ্য যে এখনও কেউ এসিড ছুঁড়ে আমার মুখ পোড়ায়নি, আমার দুচোখ অন্ধ করেনি, আমার সৌভাগ্য যে রাস্তাঘাটে এক পাল পুরুষ আমাকে ধর্ষণ করেনি। আমার সৌভাগ্য যে আমি এখনও বেঁচে আছি। আমার যে অপরাধের কারণে আমি এত সব অত্যাচারের আশঙ্কা করছি তা হচ্ছে আমি মেয়েমানুষ। আমার শিক্ষা আমার রুচি আমার মেধা আমাকে মানুষ করতে পারেনি, মেয়েমানুষ করেই রেখেছে। এই দেশে মেয়েরা কোনও যোগতা বলেই মানুষে উত্তীর্ণ হতে পারে না।..’ এক টানে লিখে ফেলি। নাইম ময়মনসিংহে আসে লেখা নিতে। লেখাটি দেব কী দেব না তখনও ভাবছি। এও ভয় হচ্ছে নিশ্চয়ই পড়ে ওরা বলে দেবে কিμছু হয়নি। বিষম সংকোচে লেখাটি শেষ পর্যন্ত দিই, তবে দেওয়ার সময় বলি, ‘দেখ, কলাম কি করে লেখে তা তো আমি জানি না। নিজের জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি শুধু।’ শক্ত শক্ত শব্দ ব্যবহার করে বলিষ্ঠ কিছু একটা লেখা আমার দ্বারা হবে না বোধহয়। নাইম লেখাটি নিয়ে যায়, তবে আমার একটি সন্দেহ থেকে যায় আদৌ ওটি ছাপা হবে কী না। চমকে দেওয়া নাইমের স্বভাব। লেখাটি যেদিন ছাপা হয় সেদিনই সে ময়মনসিংহে আসে হাতে একটি পত্রিকা নিয়ে। দেখে বিশ্বাস হয় না এত বড় বড় লেখকদের কলামের পাশে আমার কলাম। এরপর প্রতি সপ্তাহেই কলাম লিখতে হয়। কী লিখব কী লিখব এ নিয়ে আর খুব একটা ভাবতে হয় না। লেখা ছাপা হওয়ার পর থেকে আমার লেখা নিয়ে প্রচুর চিঠি আসতে থাকে খবরের কাগজ আপিসে। প্রশংসা করে, নিন্দা করে। তবে প্রশংসাই বেশি। কেউ বলে, বাহ, চমৎকার। কেউ বলে, সাংঘাতিক। কেউ বলে, খুব সত্য কথা। কেউ বলে, মেয়েটি খুব সাহসী। কেউ বলে, কলাম পড়ে আমি কেঁদেছি। কেউ নাক সিঁটকায়, বলে, এসব ওর ব্যক্তিগত ব্যপার। কেউ বলে, পুরুষ বিদ্বেষী। যে পড়ে সে-ই বলে, কিছু না কিছু বলেই।
আমার কলাম নিয়ে কাগজ আপিসে, আপিসের বাইরে প্রেসক্লাবে, সাহিত্যের আড্ডায় নাকি আলোচনার ঝড় বইছে, নাইম জানায়। পাঠক নাকি সাংঘাতিক খাচ্ছে আমার কলাম। কী লিখলে পাঠক খায়, কী লিখলে খায় না তা আমার জানা নেই। পাঠক খাওয়ানোর উদ্দেশ্য আমার নয়। প্রতিটি কলাম লিখতে লিখতে আমি জানি আমার চোখ ভিজে ওঠে জলে। প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি শব্দ আমার কলম থেকে নামে না, হৃদয় থেকে নামে। কষ্ট গুলো বুকের ভেতরে জমা কষ্টের ঝাঁপি খুলে বেরোয়। আমার নিজের দেখা আশপাশ নিয়েই মূলত লিখি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদ বড় বড় প্রবন্ধের বই লিখেছেন, নতুন একটি প্রবচনের বইও লিখেছেন, মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর নিজের অশ্লীল মন্তব্যগুলোর নাম দিয়েছেন প্রবচন। দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী হুমায়ুন আজাদের ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মেয়েই পতিতা। এসব বলে তিনি তাঁর পুরুষভক্তদের কাছ থেকে বাহবা পান, নিজেও দেঁতো হাসি হেসে বাহবা উপভোগ করেন। তিনি যত বড় লেখকই হন, তাঁকে ছেড়ে কথা কই না আমি। এমন কি যে সৈয়দ শামসুল হকের যে চরিত্র আমি দেখেছি, সেই চরিত্র সম্পর্কে আমার যে মত, তাও প্রকাশ করি। প্রকাশ করি এইজন্য যে, সাহিত্য জগতের বড় বড় অনেক রুই কাতলার আচরণ যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কোনও বদ পুরুষের আচরণের চেয়ে খুব বেশি পৃথক নয় তা বোঝাতে। যে জগতে আমার বিচরণ, সেই জগতের কথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করলেও সমাজের সব স্তরের মেয়েদের প্রতি পুরুষের আচরণও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমার ব্যক্তিগত ব্যপার তখন আর আমার ব্যক্তিগত থাকে না, সমষ্টিগত হয়ে যায়। আমি খুব নিজে লক্ষ্য করি না, কিন্তু লোকে বলে আমার ভাষা খুব ধারালো, মেয়েদের নিয়ে অনেকে অনেক কথা ই এ যাবৎ লিখেছে কিন্তু এমন করে কেউ লেখেনি।
নাইম একসময় জানালো আমার লেখা ছাপা হলে পত্রিকার কাটতি বেড়ে যায়। অবাক লাগে। বিশ্বাস হতে চায় না। এমন কাণ্ড কি ঘটে বা ঘটতে পারে! কিন্তু পারে। খবরের কাগজে হুমায়ূন আজাদের কলামটি বেশ জনপ্রিয় ছিল, তাঁর লেখা পড়ে পাঠকরা প্রচুর চিঠি লিখত, সে সব ছাপাও হত। এখন কেন তাঁর কলাম সম্পর্কে চিঠি ছাপা হয় না, তসলিমার লেখা বিষয়ে বেশির ভাগ চিঠি ছাপা হয়, এ নিয়ে হুমায়ুন আজাদ অভিযোগ করলেন, ক্ষেপে আগুন তিনি। পত্রিকার লোকেরা বলে দিয়েছে, তসলিমার বাহিরে অন্তরে কলামের আলোচনা সমালোচনা করেই মানুষ আজকাল বেশি লেখে, আপনি আপিসে নিজে এসে দেখে যেতে পারেন চিঠির স্তূপ। তারপরও নাকি ভীষণ চেঁচামেচি। এত নাম আছে লোকটির, তারপরও নাম চাই। তিনি গভীর ভাবে বিশ্বাস করেন, এ দেশে সব খারাপ লেখক, এক তিনিই শুধু ভাল। তিনিই একমাত্র কবি। আর যারা কবিতা লেখে, সবাই অকবি। শেষ অবদি এমন হল যে তিনি নিজের লেখার প্রশংসা করে ছদ্মনামে চিঠি পাঠাতে লাগলেন খবরের কাগজের চিঠিপত্র কলামের জন্য। যে লোকটি দিয়ে তিনি কলাম পাঠান কাগজ আপিসে, সেই লোকই সেসব চিঠি বহন করে নিয়ে আসে। হায় কাণ্ড, মহীরূহরা তুচ্ছ তৃণকে ঈর্ষা করছেন!
খবরের কাগজের কলামগুলোর কারণে অনেক অভাবনীয় কিছু ঘটতে লাগল। বিদ্যাপ্রকাশের খোকা আমার বই ছাপার জন্য পাগলের মত খুঁজতে লাগলেন আমাকে। অন্য পত্রিকা থেকে কলাম লেখার আমন্ত্রণ এলো। নাইমের বিশেষ অনুরোধে খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোথাও লেখা থেকে বিরত রইলাম কিন্তু বিদ্যাপ্রকাশ থেকে বই বের হল। একটি নয়, দুটি। নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে আর আমার কিছু যায় আসে না। যেহেতু নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে সকাল প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে, সেটি প্রথম দিই নি। আমার কিছু যায় আসে নার পাণ্ডুলিপি দেওয়ার পর খোকা আবদার করলেন নির্বাসিত বাহিরে অন্তরেও দিতে হবে। দুটো কবিতার বই ছাপতে না ছাপতেই বিক্রি হয়ে গেল। খোকা ব্যস্ত নতুন মুদ্রণে। নতুন মুদ্রণও শেষ হয়ে আসে কদিনেই। তিনি মুদ্রণ দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। কোনও কবিতার বই এভাবে বিক্রি হতে বাংলাবাজারের কোনও প্রকাশকই দেখেনি আগে। এমন কি সৈয়দ হকও বইমেলায় বিদ্যাপ্রকাশের স্টলে গিয়ে রাগ দেখিয়ে এসেছেন, কারণ তাঁর বইএর চেয়ে তসলিমার বই ভাল চলছে। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে সৈয়দ হকের মত বড় লেখক এ নিয়ে রাগ করতে পারেন। তাঁর সঙ্গে আমার কোনও তুলনা হয় না এ তিনি নিজেও জানেন। যে সৈয়দ হক নিজে চিঠি লিখে আমাকে পাঠিয়েছিলেন বিদ্যাপ্রকাশের কাছে, তাঁর বরং খুশি হওয়ার কথা আমার বই ভাল চললে। খোকা জানালেন, সৈয়দ হক অখুশি।
খবরের কাগজের সাফল্যের পর নাইমের একটি পরিকল্পনা ছিল একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার। নাইম যা পরিকল্পনা করে, তা সে যে করেই হোক করে ছাড়ে। ঠিক ঠিকই একদিন সে আজকের কাগজ নাম দিয়ে একটি দৈনিক পত্রিকা বের করে ফেলল। ধানমণ্ডিতে কাজী শাহেদ আহমেদর বিশাল বাড়িটির দোতলায় যে ছোট একটি ঘর বরাদ্দ ছিল খবরের কাগজ আপিসের জন্য, সেটি বড় হতে হতে বিশাল হয়ে উঠল। অনেক সাংবাদিক, অনেক টেবিল, অনেক চেয়ার। খবরের কাগজ সাপ্তাহিকীটির মত আজকের কাগজ দৈনিকটিও খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠল।
আমার কবিতার বইদুটো অভাবিত সাফল্য পাচ্ছে। কলামের কারণে খবরের কাগজের বিক্রি বেড়ে গেছে, প্রশংসা করে হাজার হাজার চিঠি আসছে কাগজ আপিসে। এসব যখন ঘটছে, ময়মনসিংহে কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম। নাইম প্রায়ই ময়মনসিংহে চলে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে, বার কয়েক তাকে অবকাশে দেখার পর বাবা বলতে শুরু করেছেন, ‘কে এই ছেলে, কী এত মাখামাখি এর সাথে! বাড়ির সবার মুখে চুনকালি দিয়া বিয়া করছিল নিজের ইচ্ছ! মত। তারপর কি হইল? জামাইয়ের সাথে তো দুইদিনও টিকতে পারে নাই। এহন আবার কোন ব্যাডার সাথে ঘুরাঘুরি করে? মাইনসে তো বেশ্যা কইব এরে। কোনও পুরুষ মানুষ আমার বাসায় যেন না আসে।’ মা বলেছিলেন ‘নাইম নামের ছেলেডা নাকি ওর বন্ধু।’ বাবা দাঁত খিঁচিয়ে বলেছেন, ‘বন্ধু আবার কী! বন্ধু জিনিসটা কি, শুনি? কোনও ছেলের সাথে আমি যেন মিশতে না দেখি। মিশতে হইলে যেন বিয়া কইরা লয়। আমি যদি আমার বাসায় কোনও ব্যাডারে দেখি, ঘাড় ধইরা বাসা থেইকা দুইডারেই বাইর করে দিব।’ অপমান আমাকে কামড়ে খায়। মা বলেন, ‘তর বাপে তরে বিয়া করতে কইছে। বিয়া ছাড়া এই যে মিশছ ব্যাডাইনগর সাথে, ওরাই বা কি কয়! ওরা তো খারাপ কয়।’ এ মার গরম হয়ে বাবার কথাগুলোই চালান করা। নরম হয়ে মা আবার বলেন, ‘তুমি নিজের জীবনের কথা একটু ভাব। নাইম যদি ভাল ছেলে হয়, যদি তোমার ভাল লাগে তারে, তাইলে বিয়ার কথা ভাব। বিয়া তো করতেই হইব। সারাজীবন কি একলা থাকবা?’
নাইম এরপর ফোন করলে বলে দিই হুট করে ময়মনসিংহে যেন সে আর চলে না আসে। এরপর একদিন সে ফোনে বলে যে কাল ভোর ছটার সময় আমি যেন কালো ফটকের বাইরে বেরোই। কেন বেরোবো, কি হবে বেরোলে তার কিছুই সে বলে না। পরদিন ভোরবেলা বেরিয়ে দেখি, নাইম দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। পরদিনও একই জিনিস ঘটে। প্রতিদিন ভোরবেলা সে ভোরের ট্রেনে ঢাকা থেকে চলে আসে ময়মনসিংহে। যেহেতু তার জন্য অবকাশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, অবকাশের বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, আমাকে এক পলক দেখার আশায় তার এই দাঁড়িয়ে থাকা। অগত্যা আমাকে ভোরে উঠতে হয়, কারও ঘুম ভাঙার আগে আমাকে নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরোতে হয়, (হাতে টুথব্রাশ নিয়ে, বাড়িতে কেউ যদি হঠাৎ জেগে ওঠে ভাব দেখাতে হয় রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দাঁত মাজতে যাচ্ছি। এটি উদ্ভট কিছু নয়, পাড়ার লোকেরা অহরহ করে।) খুব আস্তে কেউ যেন শব্দ না পায় এমন করে কালো ফটক খুলে বেরোতে হয়। নাইমের সঙ্গে পাঁচ কি দশ মিনিট রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি, কোনও জরুরি কথা নয়, ওটুকুতেই সে তুষ্ট হয়ে সকালের ট্রেনেই চলে যায় ঢাকায়। এমন পাগল ছেলে আমি আগে দেখিনি। নাইমকে বলেছি, ‘তুই এমন পাগলামি করস কেন? কোনও মানে হয় না এভাবে এত দূর চলে আসার। তোর কষ্ট হয় না জার্নিতে?’
নাইম না বলে, তার নাকি মোটেও কষ্ট হয় না বরং ভোরবেলার ঘুম ঘুম নীরব জগতটি দেখতে তার খুব ভাল লাগে। প্রতি ভোরে আমার বের হওয়া সম্ভব হয় না বাইরে, ঘুমই ভাঙে না অথবা ঘুম ভাঙলেও দেখি বাবা জেগে উঠেছেন। নাইম রাস্তায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে যায়। নাইমের এই আচরণ আমাকে প্রথম ভাবায়, সে কি আমাকে ভালবাসে! নাকি আমি ছাড়া তার আর কোনও সত্যিকার বন্ধু নেই! যদি সে ভালই বাসে, কোনওদিন তো বলেনি যে সে আমাকে ভালবাসে!
অবকাশ দিন দিন আমার কাছে আরও অসহ্য হয়ে উঠছে। কারও নরম গরম কোনও কথাই আমার ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে এ বাড়ি থেকে চলে যাই কোথাও। কোথাও আমি নিজের মত করে থাকি। ইয়াসমিন চলে যাওয়ার পর বাড়িটিতে আমার আর কেউ নেই যার সঙ্গে আমি দু কথা বলে সময় কাটাতে পারি। বুকের ধন সুহৃদও নেই। বড় ফাঁকা লাগে সবকিছু। বড় হু হু করে বুক। বাড়িটিকে আর বাড়ি বলে মনে হয় না। মার নিজের জগতটি বড় সংকীর্ণ, রান্নাঘর আর পীরবাড়ি, বাবার জগতে এ বাড়ির কারও কোনও স্থান নেই, যদি থাকে কারও, সে দাদার। দাদা আরোগ্য বিতানের দায়িত্ব নেওয়ায় বাবার সঙ্গে দাদার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আরোগ্য বিতানে চুরি হল এক রাতে। দাদা সন্দেহ করলেন শরাফ মামাকে, বাবাও তাই। টুটু মামা একবার দাদার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আর ফেরত দেন নি, সে নিয়ে দাদা প্রায়ই মামাদের গুষ্ঠি উদ্ধার করেন। মাকে উঠতে বসতে টুটু মামার টাকা নেওয়ার এবং না দেওয়ার কেচ্ছ! শোনান। দাদার অনেক আচরণই বাবার মত। বাবা যেমন নানিবাড়ির কাউকে আপন বলে ভাবেন না, দাদাও তেমন। বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া। হাশেম মামা আকুয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েছেন। বক্তৃতা ভাল করতে পারেন না বলে বীর মুক্তিযোদ্ধা হয়েও ইউনিয়ন পরিষদের ওপরের কোনও ধাপে পা ফেলতে পারেন না। মুখে খই না ফুটলে আর নানারকমের প্রতিশ্রুতি, সে মিথ্যে হোক, না দিতে পারলে কারও ভোট জোটে না। হাশেম মামা তাঁর ভাতের দোকানে বসে থাকেন, দোকানেই বন্ধুদের ডেকে ডেকে রাজনীতির আলাপ করেন। দোকান করে সংসার চালাতে হয় হাশেম মামাকে। একটি ছোট্ট ঘরে বউ আর পাঁচ কন্যা নিয়ে গাদাগাদি করে থাকেন, কন্যাদের সবাইকে লেখাপড়া করাচ্ছেন। একটি মাত্র ছেলে সুমন, খুনের মামলার আসামী হয়ে আরও কজন সমবয়সী ছেলের সঙ্গে জেল খাটছে। হাশেম মামা ম্যালা টাকা ঢালছেন ছেলে যে নির্দোশ এই প্রমাণ নিয়ে হাই কোর্টে মামলা করার জন্য। কোনও অবৈধ পথে টাকা ঢালতে তিনি চান না, চাইলে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে পারতেন অনেক আগেই। মামাদের মধ্যে এক হাশেম মামারই আগ্রহ খুব আমার বই পড়ার। দেখা হলে প্রায়ই তিনি বলেন, ‘কই তোমার বই টই কিছু বাইর হইছে? দেও একটা বই দেও।’ একদিন হাশেম মামা এসে পাঁচশ টাকা ধার নিয়ে গেলেন আমার কাছ থেকে। টাকা চাইতে লজ্জা হচ্ছিল তাঁর, তারপরও উপায় ছিল না। সুমনের মামলার জন্য খরচের কোনও মা বাপ ছিল না। তবু হাশেম মামার আমার কাছ থেকে টাকা নেওয়াটি মার ভাল লাগে নি। মা মুখ কালো করে বসে রইলেন, খবরটি বাবা বা দাদার কানে গেলে মার চৌদ্দ গুষ্ঠির বাপান্ত করে ছাড়বেন। হাশেমমামাকে খুব ভালবাসেন মা, তাঁর নীতির জন্যই ভালবাসেন। নীতির কথা কইতে হাশেমমামা নিজের বাপকে ছেড়ে দেন না। এমন মানুষটিকে কেন আজ ভাগ্নীর কাছে হাত পাততে হয়! না খেয়ে থাকতে হবে, না খেয়ে থাক, তবু যেন হাত না বাড়ায় কারও কাছে। মা যতই গুষ্ঠি নিয়ে ভাল কথা বলতে চান, গুষ্ঠি নিয়ে তাঁর লজ্জাও কম নয়। মা খুব একা, মার জগতটিতে মা ছাড়া আর কেউ নেই। সংসারে যখন কোনও অঘটন ঘটে অথবা ছেলেমেয়েদের কারও কোনও গোপন সংবাদ যদি বাবা আহরণ করতে চান অথবা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চান, তবেই মার ডাক পড়ে। আজকাল মাকে তিনি পই পই করে জিজ্ঞেস করেন আমার গতিবিধি, কী করছি , কী ভাবছি, বাকি জীবনের জন্য কোনও পরিকল্পনা করছি কী না। নাকি এরকম যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবো। এরকম ঢাকা ময়মনসিংহ। এরকম আগল বাঁধনহীন জীবন যাপন। মা আমার পরিকল্পনার কথা পরিস্কার করে বাবাকে কিছু বলতে পারেন না।
বাবা বাড়ি এসে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাকে বলেন, ‘শহরে কারও কাছে মুখ দেখানো যায় না। আজকেও একটা লোক আইসা কইল, আপনার মেয়ে তো ডাক্তার হইছে, তার কি বিয়া টিয়া দিছেন? জামাই কি ডাক্তার নাকি? সে যে একটা বিয়া করছিল, তা অনেকে জানে। ব্যাডা মদারু মাগীবাজ এইসব না জাইন্যা বিয়া করছিল কেন? এহন এই মেয়েরে কেডা বিয়া করব? সব ব্যাডাই এরে লইয়া ঘুইরা বেড়াইব। বিয়া কেউ করব না। মাইনষের সামনে আমি মুখ দেখাইতে পারি না। মাইনষে জিগায়, মেয়ে বিয়ার উপযোগী হইছে তো বিয়া দেন না কেন? মাইনষে খবর জানতে চায়। কী উত্তর দিব মানুষের প্রশ্নের! মুখটা নামাইয়া রাখতে হয়। আমি কি কইরা বলব যে মেয়ে নিজের ইচ্ছ!য় বিয়া করছিল, জামাইরে ছাইড়া দিছে, এহন ব্যাডাইন লইয়া ঘুরে। মানুষে কি খবর রাখে না, ঠিকই রাখে। ছি ছি করে। কোনও ডাক্তার ছেলেরে বিয়া করলে বালা অইলো না অইলে? এতদিনে দুই তিনডা বাইচ্চা কাইচ্চা লইয়া সংসার করতে পারত।’
মা মাথা নাড়েন, হ্যাঁ পারত। আমার বয়সী মুন্নির বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে, লক্ষ্মী মেয়ের মত সুন্দর সংসার করছে। উদাহরণটি মা দেন। উদাহরণের অভাব নেই। যেদিকে তাকান মা, আমার বয়সী এমনকী আমার বয়সে ছোটোদেরও চমৎকার সংসার হয়েছে দেখেন। কেবল আমারই হয়নি।
ভীষণ উৎপাত শুরু হয় বাড়িতে। উঠতে বসতে আমাকে কথা শুনতে হয়। কেউ ফোন করলে কে ফোন করেছে, কেউ চিঠি লিখলে কে চিঠি লিখেছে, কেউ বাড়ি এলে কে এই লোক, কি সম্পর্ক, সম্পর্ক যদি ভাল হয়, তাহলে কেন এখনো বিয়ে করছি না! সারাজীবন একা কাটাবো, বিয়ে করব না এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলে বাবার কড়া হুকুম, খুব ভাল কথা, বিয়ে না করেও অনেকে মেয়েরো বেঁচে থাকে, তবে ছেলেপিলেদের সঙ্গে মেলামেলা বন্ধ করতে হবে, বান্ধবী থাকতে পারে, তবে কোনও বন্ধু নয়। কেবল হুকুম দিয়েই তিনি শান্ত হন না, জরুরি অবস্থাও জারি করেন, আমার কোনও বন্ধু নামক পদার্থ যদি এ বাড়িতে আসে, তবে তার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবেন আমাকে। ইয়াসমিনকে মেরে বাড়িছাড়া করেছেন, আমাকে তিনি মারেন না। আমার শরীরে না পড়লেও মনে পড়তে থাকে শক্ত শক্ত চাবুকের ঘা। কুঁকড়ে যেতে থাকি যন্ত্রণায়। ইয়াসমিন নেই যে বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ব দুজন রিক্সা করে শহর ঘুরতে, অথবা গানের নাচের কবিতার অনুষ্ঠানে যাবো। একা কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। ও চলে যাওয়ার পর সকাল কবিতা পরিষদও একরকম ভাঙা ভাঙা। আমি একটি অপদার্থ, অলক্ষ্মী হিসেবে প্রতিদিন চিহ্নিত হতে থাকি। রুদ্রকে বাড়ির কেউই পছন্দ করেনি, রুদ্রকে ছেড়ে আসায় সকলে প্রথম প্রথম খুশি হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে আমার ডিভোর্সী পরিচয়টিই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়ে ওঠে, আমার স্বামীহীন জীবন কারও কাছে আর তেমন ভাল লাগে না। একটি খাঁচা না হলে যেন আমাকে আর মানাচ্ছে না। খাঁচাহীন নিরীহ জন্তুটিকে খেয়ে ফেলবে যে কেউ, তাই কোনও একটি যেন তেন খাঁচায় আমাকে যে করেই হোক ঢুকতেই হবে। এফসিপিএস এ পড়ার জন্য আমার কোনও আগ্রহ নেই, আমি একটা যাচ্ছেত!ই ভবিষ্যত গড়ে তুলছি আমার, এসব নিয়ে বাবা এত বিরক্ত যে জঘন্যতম নোংরা কথা বলতে তাঁর আর বাঁধে না এখন। আমার মনে হতে থাকে যে স্বামী সংসার না থাকলেও একটি মেয়ে যে ভাল হতে পারে, তা প্রমাণ করার একটিই উপায়, কিছু অর্জন বা বর্জন। কিছু বাড়তি যোগ্যতা। কিছু বাড়তি দক্ষতা। বর্জনের মধ্যে পুস্টিকর আহারাদি বর্জন, সাধ আহলাদ আরাম আয়েস বর্জন, বিধবারা যা করে থাকে। অথবা সন্ন্যাস বরণ। অথবা আত্মহত্যা। অথবা চিতায় ওঠা। অর্জনের মধ্যে অসামান্য সাফল্য লাভ করা কোনও কিছুতে। কোনও কিছুর শীর্ষে ওঠা। সবোগচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া। এফসিপিএস পাশ করা। এফসিপিএস এর আবরণে স্বামীহীনতার গ্লানি আমাকে ঢাকতে হবে। অসাধারণ কোনও যোগ্যতা বা দক্ষতা দেখাতে হবে আমার অস্বাভাবিক জীবনকে সহনীয় করার জন্য। যেন বয়স হলে স্বামী সন্তান না থাকাটা একধরনের পাপ, এই পাপ মোচন করতে হলে আমাকে প্রায়শ্চিত্য করতে হবে নির্বোধের মত খেটেখুটে বড় একটি ডিগ্রি নিয়ে। স্বামীহীনতা একটি যেন বিশ্রি ঘা, এটিকে ঢেকে রাখতে হলে আমার একটি মূল্যবান রঙিন চাদর চাই। আমি যেমন আছি তেমন থেকে আমার পাপ মোচন করতে পারবো না। গ্লানি দূর করতে পারবো না। কারও ক্ষমার যোগ্য হব না। অন্য কোনও মেয়ের এই বাড়তি যোগ্যতা না থাকলেও চলে, না থাকলে তাদের কেউ মন্দ বলবে না। কিন্তু স্বামীকে ছেড়েছো যখন, তোমার কয়েক ধাপ ওপরে উঠতেই হবে অন্য মেয়েদের চেয়ে। কয়েক ধাপ ওপরে উঠেই অন্য মেয়েদের কাতারে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করবে। কী জানি, তারপরও কি অর্জন হয়! পঞ্চম শ্রেণী পাশ করা স্বামীর সংসারে গতর খেটে মরা একটি মেয়ের দিকে তো এত করুণ আর এত নিস্করুণ দৃষ্টি নিয়ে কেউ তাকায় না, আমি ডাক্তার হওয়ার পরও কেবল আমার স্বামী নেই বলে আমার দিকে যেভাবে তাকায়!
পরিবার পরিকলল্পনার পরিকল্পনাহীন দপ্তরে যা ইচ্ছে তাই হচ্ছে, ওষুধ চুরি, টাকা চুরি, পুরুষ কর্তাদের আধিপত্য, সুন্দরী কোনও কর্মী দেখলেই হাত বাড়ানো। এসবের বিরুদ্ধে উচ্চয়রে কথা বলতে গিয়ে দেখি আমি একা। আমি হেরে যাচ্ছি। পুরুষ কর্তারা আমাকে হেনস্থা করার জন্য ওত পেতে থাকেন। গ্রামে গঞ্জে ক্যাম্প করে যখন লাইগেশন বা টিউবেকটমি করি, বেশ ভাল লাগে, কোনও একটি কাজের মধ্যে থাকলে সাংসারিক দুঃখ শোকগুলো সরিয়ে রাখা যায় দূরে। ক্যাম্প যদি না না থাকে তবে আপিসে যাও, বসে থাকো, কে কেমন আছে দেখ, কে কী বলে শোনো, মাছি মারো বসে বসে। কোনও একদিন হারুন-উর-রশিদ, বড়কর্তা ওরফে ডিপুটি ডিরেক্টর, যাকে লোকে ডিডি বলে ডাকে, বিকেল পাঁচটায় অনেকটা প্রমোদবিহারে যাওয়ার মত পানে মুখ লাল করে, লাল চশমা পরে দেখতে গেলেন কালিবাড়ির টিনের ঘরটি। টিনের ঘরে মুজিবর রহমান আর আম্বিয়া কপোত কপোতির মত সময় কাটাচ্ছেন। বাকিরা সব বাড়ি চলে গেছেন। সাইদুল ইসলাম নেই। তিনি নেই, তাঁর না থাকার একশ একটা কারণ আছে, কিন্তু আমি নেই কেন! ঢাকার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন নালিশ। কেবল একবারই নয়, ঘন ঘন তিনি আমার বিরুদ্ধে নালিশ করছেন। তাঁর আর সইছিল না তাঁর মধুর আহবানকে যে আমি হেলা করেছি সেই অপমান। তিনি তাঁর আকুয়ার আপিসে আমাকে প্রায়ই যেতে বলতেন। আমি গিয়েছিলাম একদিন। তিনি আমাকে তাঁর আপিসে ঘরে বসিয়ে বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে দাঁড় করিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি খাবেন, দুধ চা না রং চা?’
‘রং চা।’
‘একটা দুধ, একটা রং।’ বেয়ারার দিকে চোখ। বেয়ারা আদেশ মাথায় নিয়ে চলে গেল।
‘রং চা খান কেন? রং চা খেলে তো গায়ের রং নষ্ট হয়ে যায়। আপনারা মেয়েমানুষ, রং এর কথা তো ভাবতে হবে। হা হা।’ কুমড়োর ওপর বসানো বত্রিশটি শুকনো সীমির বীচি।
‘খেয়ে অভ্যেস বলে খাই। .. রংএর কথা আমি অত ভাবি না।’
‘সুন্দরী মেয়েদের অবশ্য অত কিছু না ভাবলেও চলে। হা হা।’
প্রসঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে ফেরাই, ‘আমাকে যে আসতে বলেছেন, কোনও কাজ আছে স্যার?’
‘কী আর কাজ! ফ্যামিলি প্ল্যানিংএ আবার কোনও কাজ থাকে নাকি.. হা হা হা।’
‘তাহলে যে আসতে বলেছেন, কোনও দরকারে?’
‘বসেন গল্প করি। আমার ওয়াইফ বাচ্চাদের নিয়ে ঢাকায় গেছে কয়েকদিনের জন্য। আপনি একদিকে ভালই আছেন। লাইফ এনজয় করতে পারছেন। ফ্যামিলি থাকলে লাইফ এনজয় করা যায় না।’
আমি চোখ নামিয়ে চা খাওয়ায় মন দিই।
‘আপনি কি খুব শাই নাকি!’
‘না তো!’ চোখ ওঠাই।
‘আপনিই যদি শাই হন, তা হইলে আর মেয়েরা কি হবে বলেন।’
আমার চোখ দেয়ালে, দেয়ালের টাঙানো ছবিতে। দূর থেকে ছবির অনেক কিছু চোখে পড়ে না কিন্তু এমন ভাবে তাকিয়ে থাকি যেন ছবির খুঁটিনাটি গুলো আমার এখন না উদ্ধার করলেই নয়।
‘আপনার কথা এইবার কিছু বলেন। আপনি তো দেখছি কথাই বলতে চান না। আপনার জীবন তো খুব ইন্টারেস্টিং জীবন! ঠিক না?’
‘ কই না তো! আমার জীবন খুব সিম্পল..’
‘কী বলেন! আমি তো শুনি মানুষের কাছে, বেশ ইস্টারেস্টিং লাইফ আপনার। আপনি তো অনেকটা ড্যাম কেয়ার। এই ক্যারেকটারটা অবশ্য ভাল। হা হা হা।’ সীমির বীচিগুলো ঝলসে ওঠে।
‘স্যার, ক্যাম্প ট্যাম্প কিছু হবে নাকি শিগরি!’ জানি ক্যাম্প আছে আগামী বুধবারে। তবু জিজ্ঞেস করি।
‘ক্যাম্প? হ্যাঁ তা আছে। নেক্সট ক্যাম্পে আপনি তো আমার গাড়িতেই যেতে পারেন। আপনি চলে আসবেন সকালে। আমার সঙ্গে যাবেন আপনি।’
‘আমার তো যাওয়ার কোনও অসুবিধা নাই..’
‘আপনি তো একদিন ডাক্তার সাইদুলের সাথে তার মোটর সাইকেলে গেলেন.. হা হা হা। মোটর সাইকেলের চেয়ে তো জিপে যাওয়া ভাল। আরামের যাওয়া।’
আমি চুপ করে থাকি।
‘তা বলেন, লাইফএর প্ল্যান কি আপনার?’
‘না, কোনও প্ল্যান নাই।’
‘প্ল্যান নাই! বিয়ে টিয়ে করবেন না?’
‘নাহ!’
‘বলেন কী! এইভাবে ইয়াং বয়সটা নষ্ট করে দিবেন নাকি!’
‘নষ্ট হবে কেন! লেখালেখি করি অবসর সময়ে। এইভাবেই তো ভাল।’
হাসির চোটে কুমড়ো নড়ছে।
‘ও আপনি তো আবার কবি।..ভাবুক মানুষ। হা হা হা’
পরিবার পরিকল্পনার বড়কর্তা আমাকে আরও অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখেন। আরও অনেকক্ষণ অর্থহীন কথাবার্তা বলেন। অর্থহীন হাসেন। আমি যতবারই উঠে আসতে চাই, ততবারই তিনি বসতে বলেন। শেষ পর্যন্ত, জরুরি কাজ আছে বলে আমাকে উঠতে হয়। যখন উঠছি, বলেন, ‘আপনি পরশু বিকালে চলে আসেন। আমি কাজ টাজ সেরে ফ্রি হয়ে থাকব। আমার ওয়াইফ ফিরবে আর সাতদিন পর। সুতরাং কোনও অসুবিধা নাই।’
পরশু বিকেলে কেন, আমি কোনওদিনই আর তাঁর আপিসে যাইনি। তাঁর আর সইছিল না আমার স্পর্ধা। তাঁর আর সইছিল না তাঁর অশোভন আহবানে সাড়া না দেওয়ার জন্য সুন্দরী কর্মীদের আমার ইন্ধন যোগানো। এই ময়মনসিংহ থেকে তিনি আমাকে সরিয়ে দেওয়ার যতরকম ষড়যন্ত্র সম্ভব, করে যাচ্ছেন। বাড়ির বাইরে ডিডির বিরোধিতা, বাড়িতে বাবার —- আমাকে কাবু করতে করতে এমন অবস্থায় ফেলল যে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হতে থাকে।
ইয়াসমিনের ওপর যত অভিমান ছিল, সব অভিমান একদিন ধুয়ে মুছে ওর কাছে যাই, ওকে দেখি আর সেই সচল সজল উচ্ছল উতল দিনগুলোর কথা ভাবি। দিনগুলো কখনও আর ফিরে আসবে না। ইচ্ছে করে ইয়াসমিনকে নিয়ে এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই কোথাও, কিন্তু শৃঙ্খলে ও নিজেকে এত বেশি জড়িয়েছে, এত বেশি আপোস করে জীবন যাপন করতে চাইছে যে ওকে নিয়ে কোথাও এক পা যাওয়া সম্ভব হয় না। ‘চল ঘুরে আসি, চল আগের মত। চল কথা বলি, হাসি, চল আগের মত।’ আমার এইসব আবদার অনুরোধ এখন আর ওকে স্পর্শ করে না। গৃহবধূ তার গত জীবনের ইতি টেনেছে, এই জীবনটি ওর স্বপ্নের ধারে কাছে না হলেও ও আর বদনাম কামাতে চায় না। এক বোনের সংসারহীন জীবনের বদনামই যথেষ্ট সংসারে। আরেক বোন না হয় প্রায়শ্চিত্যই করল নিজের জীবন দিয়ে। শ্বশুরবাড়ির চৌহদ্দিতে ইয়াসমিন বন্দি। আমি ঘন ঘন ওর শ্বশুর বাড়িতে যাই, তা ও চায়ও না। বুঝি আমাকে নিয়ে ও বাড়িতে মুখরোচক কথা হয়। এ বয়সে সকলে ঘর সংসার করে, সকলের স্বামী থাকে, আমারই নেই, আমি মানুষটি ঠিক স্বাভাবিক নই, এসব। আমার বিয়ে ভেঙে গেছে, আমি পাপী তাপী নষ্ট ভ্রষ্ট মেয়ে, এসব। আমার সঙ্গে লক্ষ্মী গৃহবধূর এত মাখামাখি থাকবেই বা কেন! তাই মাখামাখিতে যায় না ও। ওর মাখামাখি শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে, ওর মন শ্বশুরবাড়ির মানুষের মন যোগাতে। বাবাকে বলে শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের নেমন্তন্ন করায়। মা ভুতের মত রান্না করেন। কদিন পর পরই ইয়াসমিন তার শাশুড়ি, স্বামী, ভাসুর, আর ভাসুরবউদের নিয়ে অবকাশে এসে নেমন্তন্ন খেয়ে যায়। ভারত থেকে আনা জিনিসপত্রগুলো ইয়াসমিনকে দিয়ে দিই, ও খুশি হয়। সোনার গয়নাতেও আকর্ষণ নেই আমার, গয়নাগুলোও দিয়ে দিই, ওর চোখ ঝিকমিক করে আনন্দে।
জানি দুঃসময় ঝাঁক বেঁধে আসে। কিন্তু ঝাঁক বেঁধে আসতে থাকলেও তো সীমা থাকে সব কিছুরই। কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া দুঃসময় আমার ওপর ভারী ভারী পাথরের মত পড়তে থাকে। চূড়ান্ত দুঃসময়টি আসে এক সকালে। তিরিশ হাজার টাকা ধার নিয়ে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা শোধ করেছি, বাকিটা এখনও শোধ করছি না বলে আবদুল করিম তুলকালাম কাণ্ড বাঁধান অবকাশে। আমি তাঁর টাকায় বেড়াতে গিয়েছি ভারতে, আমি একটা বদমাশ মেয়ে মানুষ, আমার মত খারাপ তিনি ইহজীবনে কাউকে দেখেননি ইত্যাদি বলে বাড়ি মাথায় তোলেন। আবদুল করিমের কাছ থেকে ভারত যাওয়ার আগে টাকা ধার নিয়েছিলাম, কিন্তু ফেরত দেওয়ার কথা ছিল প্রতিমাসে মাইনে পেয়ে। তিনি রাজি হয়েছিলেন, আর এখন হুট করে বাকি সবটা টাকাই একবারে চাচ্ছেন। এই আবদুল করিমও কম কৌশল করেননি আমাকে নাগাল পেতে। বুঝতে দিইনি কখনও, যে, আমি বুঝতে পারছি তাঁর কৌশল। ফুল ফুলের চারা দেখাতে আবদুল করিম একদিন আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ছোটবাজারের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে। সাদা মনে সেই বাড়িতে গিয়ে দেখি সবুজ পাঞ্জাবি পরা, পকেটে টাকার বাণ্ডিল নিয়ে ঘোরা মধ্যবয়সী ব্যবসায়ী আর আবদুল করিম বসে আছেন একটি অন্ধকার অন্ধকার ঘরে। ব্যবসায়ীটির অনেক টাকা, আমার টাকা পয়সার দরকার হলে তাঁর কাছে চাইলেই দিয়ে দেবে, এমনকী শোধ না দিলেও চলবে এধরনের কথা যখন আবদুল করিম বলছিলেন, যেন বুঝিনি তিনি কি ইঙ্গিত করছেন, হেসে, চা খেয়ে, সবুজ পাঞ্জাবির সবজি-বাগানের ব্যবসা নিয়ে সাধারণ কিছু আলাপ করে আমার হাসপাতালে যাবার তাড়া আছে এক্ষুনি না গেলেই নয় বলে বেরিয়ে এসেছি। এই আবদুল করিমই অবকাশে এসে আমাকে ডেকে একদিন বলেছেন, ‘ডাক্তার, আমার একটা অসুখ আছে, কী করা যায় বল তো!’ কি অসুখ জানতে চাইলে তিনি গলা চেপে বলেন, তাঁর সেক্সুয়াল ডিজায়ার অত্যন্ত বেশি, দুই বউএর কেউই তাঁকে হ্যাপি করতে পারছে না, তিনি যত বেশি চান, তারা তত বেশি মিইয়ে যায়, তিনি স্টে করেন অনেকক্ষণ, তারা খুব তাড়াতাড়িই ফিনিশ। শুনে, এ যেন হরহামেশা হচ্ছে এমন সহজ রোগ, যেন সর্দি জ্বর, যেন আমাশা, যেন অম্বল— কান নাক চোখ ঠোঁট যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রেখে অত্যন্ত সহজ সুরে, টাক মাথা, উপরি টাকায় পকেট বোঝাই করা, পান-দাঁতে হাসা, হাসিতে ভুঁিড় কাঁপা লোকটির চিকিৎসা করি, চিকিৎসা বলতে উপদেশ ‘এ তো এমন কোনও সমস্যা না, আপনি যৌনরোগবিশেষরি কাছে যান, ওখানে ভাল ট্রিটমেন্ট পাবেন, আমি তো যৌনরোগের বিশেষজ্ঞ না।’
‘কী বল, তুমি ডাক্তার হইছ, তুমি ট্রিটমেন্ট করতে পারবা না কথা হইল!’
‘আপনের যে রোগ করিম ভাই, তার জন্য বিশেষজ্ঞ দরকার।’
‘কী যে বল, তুমি হইলা আপন মানুষ, আত্মীয়। বাইরের ডাক্তারের কাছে এইসব বলা যাবে নাকি!’
‘কেন যাবে না? রোগ তো রোগই।’
‘নাহ, এই রোগ কোনও ডাক্তারে সারাইতে পারবে না।’
‘আমি তো ডাক্তার, আমার কাছে তাইলে বললেন কেন!’
ফ্যাক ফ্যাক করে হাঁসের মত হেসে করিম বললেন, ‘আমার চিকিৎসা কি তা আমি জানি।’
কি চিকিৎসা তা জিজ্ঞেস করি না, তিনি নিজেই বলেন, ‘আমার একটা ইয়ং মেয়ে দরকার।’
আমি বলি, ‘কিরণ আর কুমুদ তো আছে, আপনের দুই মেয়ে। ইয়ং মেয়ে।’
করিম জিভে কামড় দিয়ে বলেন, ‘ওরা তো আমার সন্তাান। বলতাছি আমার নিজের জন্য।’
‘ও তাই বলেন!’
না বোঝার এই ভানটুকু আমার না করলেই নয়। আমি লোকটিকে জুতোপেটা করে বাড়ি থেকে তাড়াতে চাই না, লোকটি এবাড়ির আত্মীয়। কিন্তু লোকটিকে বুঝতে দিতেও চাই না যে তাঁর কোনও ইঙ্গিত আদৌ আমার বোধগম্য হয়েছে। আমি বুঝেছি তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা যদি তিনি বোঝেন, তবে এটুকুই তাকে যৌনতৃপ্তি দিত হয়ত। ভানটুকু করেছি, কারণ, তাঁকে, যত কুকথাই তিনি বলুন, ভাল মানুষ হিসেবেই বিচার করি, তিনি যে কোনও অশোভন ইঙ্গিত দিতে পারেন তা যে আমি কল্পনাও করতে পারি না, তাও বোঝানো। এটুকু যদি তাঁকে অন্তত আমার সঙ্গে আর কখনও এমন আলাপচারিতায় আগ্রহী না করে, যে আলাপের রস গ্রহণ করার মত যোগ্যতাও আমার নেই।
সেই করিম।
সেই আবদুল করিম।
বাড়ি মাথায় তুলছেন চেঁচিয়ে। আমি খারাপ মেয়ে। আমি তাঁর টাকায় লাঙ নিয়ে ফুর্তি করে এসেছি। আমি মৌজ করে এসেছি, আমোদ করে এসেছি। এইসব খারাপ চরিত্রের মেয়েদের যে কেউ চাইলেই পেতে পারে! ইত্যাদি ইত্যাদি।
মা ধমকে থামান করিমকে। বলেন, ‘বাজে কথা বলতাছো কেন! টাকা ধার নিছে। টাকা দিয়া দিবে। আজ না পারে, কাল দিবে, এইজন্য এইসব কথা বলার তুমি কে?’
করিম থামেন। ওদিকে হাসিনা কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে করিমের প্রতিটি কথা শুনে যাচ্ছিল, কোনও রকম প্রতিবাদ করেনি। করার কোনও কারণ নেই, কারণ তার একধরণের আনন্দই হচ্ছিল কথাগুলো শুনতে। এরকম মোক্ষম সুযোগ ছেড়ে দেওয়ার সে কোনও মানে দেখে না।
যখন ইয়াসমিন ঘরে ঢোকে মিলনকে নিয়ে, করিম চলে গেছেন। গয়নাগাটি আমার যেখানে যা ছিল বের করে নিয়ে যাই সোনার দোকানে, ইয়াসমিন সঙ্গে যায়। যত দাম সোনার, তার চেয়ে অর্ধেক দাম বলে দোকানী, সেই দামেই দিয়ে দেখি কুড়ি হাজার টাকা হচ্ছে। ইয়াসমিন মিলনের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়ে দেয়। পঁচিশ হাজার টাকা সেদিনই হাসিনার হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁর ভদ্রলোক বোন জামাইকে যেন দিয়ে আসে। টাকা হাতে পেয়ে হাসিনার মুখে কোনও স্বস্তির ছোঁয়া দেখা যায় না, যেন আমি দীর্ঘদিন এই দেনায় বেঁধে থাকলে তার আনন্দ হত।
আমি পালাই ময়মনসিংহ থেকে। শ্বাস নিতে যাই কোনও শুদ্ধ হাওয়ায়। ঢাকায় গীতার দুর্ব্যবহার যথারীতি চলে। ঢুকতে দেয় তো বসতে দেয় না, বসতে দেয় তো শুতে দেয় না। সুহৃদকে নাগাল থেকে সরিয়ে রাখে। সুখের সময় গীতা হয়ত পিঁড়ি দেয় বসতে, দুঃখের সময় দূর দূর করে তাড়ায়। গীতার যে কত রকম নিয়ম আছে অপদস্থ করার, তা বোঝার সাধ্য থাকে না আমার। নাইমের কাছে যাই ভাঙা মন নিয়ে। হীনতা স্বার্থপরতা আর কুটকচাল এসব তার নেই তো নেই ই, বরং কী করলে আমি খুশি হব, কী করলে আমি তাকে বেশ বুদ্ধিমান মনে করব, কী করলে মনে করব তার কোনও সংকীর্ণতা নেই, কী বললে মনে করব নারী পুরুষে যে কোনও রকম বৈষম্যের সে বিরোধী, প্রগতিশীল রাজনীতিতে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী, কী বললে তাকে অসাম্প্রদায়িক ভাবব, কী করলে তাকে স্বচ্ছল, স্বচ্ছ, উদার, উচ্ছল, প্রাণবান বলে ভাবব এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হব, তার সবই সে করার বলার প্রাণান্ত চেষ্টা করে যায়। নাইমের এত চেষ্টার পরও তার প্রতি আমার জন্য কোনও ভালবাসা জন্ম নেয় না। আমার অনাথ অভুক্ত অবাধ অসার শরীরটি নাইমের স্পর্শে স্পর্শে যেদিন জেগে ওঠে, সেদিনও তার জন্য আমার কোনও প্রেম জাগে না। চল বিয়ে করি! নাইম বলে সেই বিকেলেই, যে বিকেলে শরীর জাগে। বাক্যটি এমনভাবে সে বলে যে মনে হয় সে অন্য যে কোনও দিনের মত চল চা খাই, চল মেলায় যাই বা চল ঘুইরা আসি বলছে। বাক্যটি আমাকে মোটেও চমকে দেয় না। নাইমের যে কোনও প্রস্তাবে আমি রাজি হই, যেহেতু আমি জানি যে সে আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, জানি যে পৃথিবীর আর কেউ চাইলেও সে আমার কোনও অমঙ্গল চায় না। নাইমকে আমার কোনও খাঁচা বলে মনে হয় না। লাঞ্ছনা আর অপমানের পুঁতিগন্ধময় পরিবেশ থেকে নাইম আমার জন্য একরকম মুক্তি।
সেই বিকেলেই ধানমণ্ডির দিকে রিক্সা করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রাস্তার পাশে ছোট্ট একটি ঘরে নাইম থামে, ঘরটির মাথায় ছোট একটি নোটারি পাবলিক লেখা সাইনবোর্ড ঝোলানো। স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরটিতে ভূুতের মত একটি লোক বসা ছিল, নাইম জিজ্ঞেস করল বিয়ে করতে হলে কি করতে হয়। দুজনের দুটো সই, আর কিছু টাকা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সইও হল, টাকাও দেওয়া হল। সে রাতে নাইমের ইস্কাটনের বাড়িতে ফিরে দুজনের শোয়া হল, প্রথম শোয়া। শুতে হলে কি সই করে শুতে হয়! সই না করেও তো হয়! সই ব্যপারটিকে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে মনে হয় না। আপিসের কাগজপত্রে সই চাইলেই সই দিয়ে দিই। আমি একটি তুচ্ছ মানুষ, আমার সই এর মূল্যই বা কী! সই হয়। এতে আমার কিছু না হলেও নাইমের হয়। শুতে হলে নাইমের সই করে শোয়ার সংস্কারটির একটি রফা হয়। ঘর ভর্তি বাবা মা ভাই বোন, বোন জামাই, ভাই বউ সবার মধ্যেই নাইম আমাকে নিয়ে পুরোটা রাত না হলেও অর্ধেক রাত কাটায়। এ বাড়িতে নাইমের অধিকার আছে যা কিছু করার। এ বাড়িতে নাইমই হল কর্তা, সে যা করে, তাতে কারও জিভে প্রতিবাদের টুঁ ওঠে না কারণ বাড়ির বাসিন্দাদের খাওয়া পরার সব খরচ নাইমই জোগায়, মন্ত বড় বাড়িটির ভাড়াও। এ বাড়িতে তার বন্ধু বান্ধবীরা অহরহ আসছে, খাচ্ছে, রাত কাটাচ্ছে। এ বাড়িতে এক রাতে আমিও থেকেছি, নাইম তার ঘরটি আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। এবারের থাকা অন্যরকম যদিও, সই করে থাকা, কিন্তু আমার মোটেও অন্যরকম মনে হয় না। যেমন বন্ধু ছিল নাইম, তেমনই থেকে যায়। তেমনই তুই তোকারি।
ময়মনসিংহে পানে লাল হওয়া জিভের, লাল চশমার,পরিবার পরিকল্পনার সুন্দরী কর্মীদের দিকে বাঁকা বাঁকা হাসি হাসা ডিজির আবেদনে কাজ হয়েছে। বদলি চৌদ্দগ্রামে। এক লাথিতে চৌদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। আমি যে খুব নিরানন্দে ভুগেছি বদলির আদেশ পেয়ে তা নয়। একরকম চাচ্ছিল!মও অবকাশ থেকে দূরে যেতে, পরিবার পরিকল্পনার অসুস্থ পরিবেশ থেকে, যে অসুস্থতার বিরুদ্ধে কোনও জীবানুনাশক কাজ করে না, চাচ্ছিল!মও সরতে। চৌদ্দগ্রাম চলে যাবো শুনে মা চিৎকার করে কাঁদলেন। কিন্তু যেতে তো হবেই। বদলির চাকরি। চৌদ্দগ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগ দিয়ে কদিন আসা যাওয়া কুমিল্লায় নাইমদের বাড়িতে থেকে করেছি। ওখানে প্রায়ই চলে যেত নাইম, ভোরে উঠে আবার ঢাকা ফিরত।
আমাকে চমকে দেওয়ার অভ্যেস তখনও যায়নি নাইমের। হঠাৎ একদিন একটি কাগজ হাতে দিল নাইম, আমার বদলির কাগজ। চৌদ্দগ্রাম থেকে দু সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের রক্তব্যাংকে মেডিকেল অফিসার পদে বদলি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি। প্রভাব বুঝি একেই বলে! আমার পক্ষে জীবনে কখনও সম্ভব ছিল না কোনও ভাল জায়গায় বদলি হওয়া, ঢাকা শহরে মোটে দুটো মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। লোকে বলে মামা কাকার জোর না থাকলে এসব জায়গায় পোস্টিং হয় না। আমার মামা কাকারা কেউ ওপরতলায় বাস করেন না। সুতরাং আমার কপালে চৌদ্দগ্রাম, পঞ্চগ্রাম, অষ্টগ্রামই ছিল। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের দৌড় খবরের কাগজ আপিস পর্যন্ত না হয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পর্যন্ত যে হতে পারে, তা কটি লোক জানে! নাইমের এই চমকটি আগের সব চমককে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্বেও তার সঙ্গে সইএর সম্পর্কটিও আমার দুমাসও টেকেনি। নাইমের ইচ্ছে ছিল একদিন ঘটা করে বিয়ের অনুষ্ঠান করবে, বন্ধু বান্ধব চেনা পরিচিত সবাইকে জানাবে বিয়ের খবর। তার এই ইচ্ছেটি সফল হয় না। একদিন রিক্সা নিয়ে ধানমণ্ডির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে ওই ছোট্ট অন্ধকার ঘরটিতে গিয়ে কিছু টাকা আর একটি সই দিয়ে আসি, এবারের সইটি আগের সইটির উল্টো। সই থাকা না থাকায় কোনও কিছু যায় আসে না। আমি সেই আগের আমি। আমার মনে হয় না কিছু হারিয়েছি বা কিছু পেয়েছি আমি। প্রথমবার এখানে সই করতে এসেও যেমন নিস্পৃহ ছিলাম, এবারও তাই। সই এর গুরুত্ব আমার কাছে বন্ধুত্বের চেয়ে বেশি নয়। বন্ধুত্ব যদি ম্লান হয়ে আসে, সেখানে কোনও সই কোনও সম্পর্ক ধরে রাখতে পারে না।
সইএর ঘটনার পর থেকেই নাইমের সংকীর্ণ, প্রতিশোধপরায়ণ, অনুদার, হিংসুক চেহারাটি ধীরে ধীরে এত প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে যে ভাবতে লজ্জা হয় এই নাইম সেই নাইম, যাকে আমি নিজের সবচেয়ে ভাল বন্ধু বলে মনে করেছিলাম। আমার ওপর কর্তৃত্ব করার স্পৃহা তাকে উন্মাদ করে তুলেছে।
আমি ময়মনসিংহে যেতে চাইলে নাইম বলে এখন যাওয়ার দরকার নাই।
মানে?
মানে হইল এখন যাওয়ার দরকার নাই।
তাইলে কখন যাওয়ার দরকার?
পরে।
পরে কবে?
আমি বলব।
যেদিন নাইম সিদ্ধান্ত নেবে সেদিন আমাকে ময়মনসিংহে যেতে হবে। যেদিন সে আমাকে বাইরে বেড়াতে নেবে, সেদিন আমাকে বাইরে বেড়াতে যেতে হবে।
সইএর আগে নাইম যেমন সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিল আমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, সই এর পর সে ব্যস্ত হয়ে যায় তার ইচ্ছের খাঁচায় আমাকে বন্দি করার জন্য। বন্দি হতে না চাইলে নাইম চিৎকার করে, দপদপ করে কাঁপতে থাকে তার কপালের শিরা। সই এর আগে তার যে গাড়িটি আমি মাঝে মধ্যে চালাতাম, সইএর পর কৌশলে সেই গাড়ির চালকের আসনে আমার বসা সে বন্ধ করে দেয়। সইএর আগে প্রতি সপ্তাহে আমার কলাম ছাপার জন্য ভীষণ আগ্রহ ছিল তার, সইএর পর সেই আগ্রহ আর থাকে না। আমি ক্রমশ নাইমের হাতের পুতুল হয়ে উঠি। আমি যদি একটি কলম চাই, নাইম আমাকে দশটি কলম এনে দেবে কিন্তু সে দেবে, আমাকে সংগ্রহ করতে দেবে না। আমার সব ইচ্ছে আকাঙ্খা নাইম মেটাতে চায়, আমাকে সে কিছুই মেটাতে দেয় না। আমাকে সে আমার জন্য অহংকার করতে দেয় না, আমার জন্য অহংকার সে নিজে করতে চায়। আমার সব দায়িত্ব সে নিজে নিতে চায়, যেখানে আমার কোনও ভুমিকা থাকবে না, কেবল তার ভুমিকাই থাকবে। সে যে আমার চেয়ে সবদিক দিয়ে বড়, তা বোঝাতে এমন মরিয়া হয়ে উঠল যে আমার কৃতিত্ব ক্রমে ক্রমে তার কাছে তুচ্ছ বিষয় হয়ে ওঠে, যে কৃতিত্ব নিয়ে তার একসময় গৌরবের সীমা ছিল না। যে নাইম নিজেকে নিয়ে হাস্যরস করত, বলত ‘আমি কিচ্ছু জানি না, আমার কোনও ধারণাই নাই, আমি হইলাম একটা গবেট,’ সেই নাইমই নিজেকে জ্ঞানের আধার, সর্বগুণে গুণান্বিত, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী বলতে কোনও দ্বিধা করে না। নিজের মহানুভবতার কথা চোখ ফুলিয়ে, নাক ফুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে, পেট ফুলিয়ে অনর্গল বলে যায়। আমার মনে হতে থাকে নাইমের আগের চরিত্রের আদ্যোপান্ত ছিল আমাকে জয় করার জন্য। আসল চেহারাটি মানুষের কোনও না কোনও সময় বেরোয়, মুখোশ একসময় খুলে পড়েই। আমাকে যে করেই হোক সে তার মুঠোয় পেয়েছে। মুঠোর মধ্যে কোনও মেয়েমানুষ এসে গেলে তাকে আর মাথা ছাড়াতে দিতে কোনও পুরুষেরই ইচ্ছে করে না। নাইম তো পুরুষই।
নাইম নিজের বাবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, প্রায়ই উল্লেখ করে বাবা তার পকিস্তান আমলে সংসদ সদস্য ছিলেন। এ নিয়ে গৌরবের কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ তার এই বাবাই কুমিল্লার দেবীদ্বারে মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময় কেবল রাজাকারই নয়, শান্তি কমিটির বড় নেতা ছিলেন। নাইম কখনও তার বাবার অতীতের ভূমিকা নিয়ে গ্লানিতে ভোগে না। একবারও বলে না যে তার বাবা ভুল করেছিলেন। বাবাকে এমনই সে ভালবাসে যে আমাকে কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর রক্তচাপ মাপতে বলে। একবার মেপে দেখেছি রক্তচাপ ঠিক আছে, পরদিনও আবার সে মাপতে বলে। পরদিনও মাপি। তার পর আবারও। আমি অবাক হয়ে বলি, কেন? নাইম বলে, এমনি। এমনি কেন? এমনি এমনি প্রতিদিন কারও রক্তচাপ মাপার তো কোনও অর্থ হয় না। বাবা তার রীতিমত সুস্থ মানুষ, রক্তচাপে কোনও ওঠানামা নেই, কিন্তু তার বাবা বলেই, বাবাকে সে ভালবাসে বলেই আমাকে খামোকা তাঁর রক্তচাপ মাপতে হবে। আমি না বলে দিই, আমি মাপবো না। নাইম রাগে থরথর করে কাঁপে। এমনিতেই তার আঙুল কাঁপে কোনও কারণ ছাড়াই। রেগে গেলে সারা গা কাঁপে। চোখ বেরিয়ে আসে গর্ত থেকে। নাইম যেমনই হোক, নাইমের পরিবারের সকলে খুব চমৎকার মানুষ। নাইমের মা দেখতে অপূর্ব সুন্দরী, সুন্দরীর স্বামীটি অসুন্দরের ডিপো। ডিপো হলেও আমি যে কটাদিন নাইমের বাড়িতে ছিলাম আমার সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেছেন। কেবল তিনিই নন, বাড়ির সকলেই আমাকে মাথায় তুলে রেখেছে। মাথায় তুললেই কি সুখ হয়!
নাইমের বিনয়ী স্বভাবে অনেকে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অহংকার তার প্রচণ্ড। নিজেকে নিয়ে যেমন, তার বাবাকে নিয়েও তার অহংকারের শেষ নেই। নাইমের রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগে। খবরের কাগজের দায়িত্ব নেওয়ার আগে সে চাকরি করত ইনকিলাব পত্রিকায়। ইনকিলাব পত্রিকাটি একশ ভাগ মৌলবাদিদের পত্রিকা। এর সম্পাদক প্রকাশক মাওলানা মান্নান দেশের নামকরা রাজাকার। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে হামেশা লিখে যাচ্ছে। দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে। নাইম এই পত্রিকাার বিরুদ্ধে একটি বাক্য উচ্চারণ করে না। বরং ইনকিলাব পত্রিকাটির মেক আপ গেট আপ, ইনকিলাবের ছাপাখানার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে। খবরের কাগজও সে ছাপে ইনকিলাবের ছাপাখানা থেকে। একদিন রাতে আমাকে নিয়ে ইনকিলাবের আধুনিক ছাপাখানা দেখিয়ে আনে। দেশে দুটি পক্ষ, একটি মৌলবাদ, আরেকটি মৌলবাদের বিরুদ্ধ। খবরের কাগজের সম্পাদকের ভূমিকায় এসে মৌলবাদের বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে তার খাতির জমে ওঠে, কিন্তু সে নিজে খুব স্পষ্ট করে কোনও পক্ষ নেয় না। ইনকিলাবের অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে সে এক আলোকিত জগতে এসেছে। সাংবাদিকতায় বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা নাইম খবরের কাগজ আর আজকের কাগজের কোনও সম্পাদকীয় আজ পর্যন্ত লেখেনি, আশেপাশের ডেস্কে বসা পাতি সাংবাদিকদের দিয়ে সম্পাদকীয় লিখিয়ে নেয়। কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতার বা কোনও কবি লেখকের কোনও সাক্ষাৎকারও সে আজ পর্যন্ত নেয়নি। এসবে তার দক্ষতা নেই। তার দক্ষতা বাণিজ্যে। কাজী শাহেদ আহমেদ তাকে পছন্দ করে সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন। বড় বড় লেখকদের জড়ো করে কলাম লিখিয়ে কাগজের বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করেছে তার ওপর জনপ্রিয়তা জুটিয়েছে। নাইম যদিও লেখালেখির জগতে উড়ে এসে জুড়ে বসা একটি নাম তার পরও তার কৃতিত্বের জন্য সে বাহবা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। এরকম হঠাৎ এসে ঝড় তোলা কম কথা নয়।
নাইমের সঙ্গে ওই শোয়াশোয়ির শুরুতেই ঘটনা বা দুর্ঘটনাটি ঘটে। রুদ্রর সঙ্গে দীর্ঘদিন শুয়েও যে ঘটনাটি ঘটেনি, তা নাইমের সঙ্গে দুদিন শুয়েই ঘটে যায়। পেটে বাচ্চা আসে। সারা শরীরে আশ্চর্য এক পরিবর্তন লক্ষ করি। মনেও। যেন এ আমি অন্য আমি। এ আমাকে আমি চিনি না। নিজের রূপান্তরিত এই অস্তিত্বটি অভাবিত এক শিহরণ সৃষ্টি করে আমার ভেতর। এই রূপটিকে আগে কখনও আমি কল্পনা করিনি। ভয়, লজ্জা, সুখ, স্বপ্ন, সব বিজলির মত চমকাতে থাকে আমার আকাশ জুড়ে। নাইম আমাকে অনেক চমকে দিয়েছে। কিন্তু এবারের চমকটি ভিন্ন। এই চমকটির কোনও তুলনা হয় না।
চল ক্লিনিকে চল।
ক্লিনিকে কেন?
এবরশন করতে চল।
মানে?
মানে কিছু না। এবরশন করতে হইব।
এবরশন করতে হইব কেন?
আরে এহনই আবার বাচ্চা কাচ্চা কি? এইসব পরে চিন্তা করলেই হইব।
আমার কোনও আপত্তি নাইম মানে না। সে আমাকে গুলশানের একটি ক্লিনিকে টেনে নিয়ে গিয়ে আমার গর্ভপাত ঘটায়। আমি জানি কেন ঘটায় সে এটি। তার ধারণা, ভ্রূণের জন্য যে স্পার্মের প্রয়োজন হয়, তা অন্য কোথাও থেকে আমি সংগ্রহ করে এনেছি। নাইমের জন্য আমার মায়া হয়, সন্দেহের মন তার নিজের বাচ্চাকে মেরে ফেলতে দ্বিধা করেনি। সন্দেহ এমনই এক ভয়ংকর আগুন, আমি পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকি। আমি কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে কথা বলছি, কে আমাকে জন্মদিনে কি উপহার দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে এসব নিয়ে সন্দেহের চোখ ক্রমশ বাঘের মত হতে থাকে, আমাকে ছিঁড়ে খেতে চায় সে চোখ। মায়া হয় নাইমের জন্য, তার সন্দেহের মন এ কথা তাকে বুঝতে দেয় না যদি কারও সঙ্গে আমার কোনও রকম শারীরিক মানসিক সম্পর্ক থেকে থাকে, তবে তা তার সঙ্গেই, আর কারও সঙ্গে নয়। নাইম ভেবেছে আমি তার সঙ্গে চালাকি করেছি, তাই সে অতি চালাকি করে আমার চালাকির জবাব দিয়েছে। মন ধীরে ধীরে নয়, খুব দ্রুতই ওঠে নাইম থেকে।
একসময় খবরের কাগজ আপিসেও শুরু হয় নাইমের অতি চালাকির বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ। কাজী শাহেদ আহমেদের ব্ল্যাংক চেক এর অপব্যবহার করেছে নাইম। কাজী শাহেদ অর্ধচন্দ্র নয়, পূর্ণচন্দ্র দিয়েই বিদেয় করেন নাইমকে। কাগজের মালিক কাজী শাহেদ নিজে সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। যে কাজীর প্রশংসায় নাইমের মুখে খই ফুটত, সেই একই কাজী সম্পর্কে সে বলে বেড়াতে লাগল তাঁর মত বদ লোক দুনিয়ায় আর নেই। কুৎসা ছাড়া আর কিছু তার মুখে ফোটে না। তাকে তার বিশালাসন থেকে নামিয়ে দেবার শোধ সে যে করেই হোক নেবে। নাইমের ঘটে বুদ্ধি কম নয়, এই বুদ্ধির জোরেই সে খবরের কাগজ সাপ্তাহিকীটি জনপ্রিয় করে আজকের কাগজ নামে একটি দৈনিকে হাত দেয়। রাতারাতি আজকের কাগজ দেশের এক নম্বর না হলেও দু নম্বর জনপ্রিয়তার তালিকায় চলে আসে, বুদ্ধি আছে, তবে সেই বুদ্ধির সঙ্গে কিছু কিছু কুবুদ্ধি সব কিছু গোলমাল করে দেয়। নাইম দমে যাওয়ার পাত্র নয়। আজকের কাগজের কাজ ফুরিয়ে গেলে সে যে বিমর্ষ বসে থাকবে তা নয়, দল বল জোগাড় করে ভোরের কাগজ নামে একটি পত্রিকা বের করে। আজকের কাগজে যে লেখকদের দিয়ে লেখাতো, অনেককে সরিয়ে নিয়ে আসে নতুন কাগজে। ভোরের কাগজ জনপ্রিয় হতে থাকে ধীরে ধীরে।
নাইম যখন বুঝতে পারে আমি আর তাকে বিশাল কিছু বলে মনে করছি না, সে উঠে পড়ে লেগে যায় প্রতিশোধ নিতে। তার বিনয় ঝুলে পড়ে মরা ডালের মত, তার ভদ্রতা নম্রতা সৌজন্য সব গ্যাসবেলুনের মত শূন্যে উড়ে যায়, সত্যিকার নাইম তার চোখ রাঙানো, দাঁত দেখানো, গলা ফাটানো নিয়ে প্রকাশিত হয়। তার কোনও আচরণ আমাকে কষ্ট দেবে কি না, ক্ষুব্ধ করবে কি না তা নিয়ে আর সে চিন্তিত নয়। আমার চেনা পরিচিত আত্মীয় বন্ধু যাকেই সে চেনে সবার কাছে গিয়ে সে আমার জন্য সে এই করেছে সেই করেছে আর আমি তার জন্য এই করিনি সেই করিনির লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে বুঝিয়ে আসে যে তার মত এত অনুগত, অনবদ্য, অসাধারণ ছেলের সঙ্গে আমি খুব অন্যায় করেছি। আমি অকৃতজ্ঞ। আমি অপয়া। আমি অশালীন। আমি অবিবেচক। আমি অপ্রকৃতিস্থ।
নাইম যখন বুঝতে পারে যে তাকে আমি র্নিদ্বিধায় ত্যাগ করতে পারি, তখন সে জোঁকের মত আমাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। যখন সে টের পায় যে তার সন্দেহের ধারে কাছে আমি আর যেতে চাইছি না, সে ফেটে পড়ে রাগে। যখন সে দেখে তার রাগের আমি মোটেও পরোয়া করছি না, সে আমাকে হেনস্থা করার পরিকল্পনা আঁটে। পরিকল্পনায় নাইম বরাবরই বড় পাকা।
মিটফোর্ড হাসপাতালের কাছে আরমানিটোলায় একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকছি। হঠাৎ একদিন দরজায় কড়া নাড়ে কেউ। খুলে দেখি নাইম। তার জানার কথা নয় আমার ঠিকানা। কিন্তু বাজপাখির চোখ ঠিক ঠিক চিনে নেয় কোথায় শিকার তার। দরজা সে এমন জোরে ধাককাতে থাকে যে আশেপাশের লোক জমে যায়। অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে এসে তাকে জানিয়ে দিই, কিছুতেই আমি তাকে ভেতরে ঢুকতে দেব না। ঢুকতে তাকে দিইনি কারণ আমি চাইনি রুদ্রকে সে একফোঁটা অসম্মান করুক। একসময় নাইম সরে যায় আমার দরজা থেকে, কিছু করার পরিকল্পনা নিয়েই সে সরে। এক, আমাকে এ বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা। দুই, সত্যিকার একটি বিয়ে করা।
০৯. সুখের সংসার
মিটফোর্ডের ব্লাড ব্যাংকে পোস্টিং আমার। রক্ত বিক্রি করার জন্য দরিদ্র কিছু লোক আসে, সেই লোকদের শরীর থেকে রক্ত কি করে নিতে হয়, কি করে রক্তের ব্যাগে লেবেল এঁটে ফ্রিজে রাখতে হয় তা ডাক্তারদের চেয়ে টেকনিসিয়ানরাই জানে ভাল। সকাল আটটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত খামোকা বসে থাকতে হয় আমার। মাঝে মধ্যে কিছু কাগজে সই করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। এরকম কাজহীন বসে থাকা আমার অসহ্য লাগে। ব্লাড ব্যাংকের পাশেই স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগ। ওখানে ডাক্তাররা দম ফেলার সময় পায় না এমন ছুটোছুটি করে কাজ করে। দেখে আমার বড় সাধ হয় ব্যস্ত হতে। দিন রাত কাজ করতে। একদিন গাইনি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বায়েস ভুঁইয়ার কাছে একটি আবেদন পত্র লিখে নিয়ে যাই। ‘আমি গাইনি বিভাগে কাজ করতে আগ্রহী, আমাকে কাজ করার অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।’ অধ্যাপক বায়েস ভুঁইয়া আমাকে বাধিত করেন।
হাসপাতালের কাছেই আরমানিটোলায় আমার বাড়ি। বাড়িটি ভাড়া নিতে আমাকে সাহায্য করেছেন বিদ্যাপ্রকাশের মালিক মজিবর রহমান খোকা। খোকার প্রকাশনায় আমার কবিতার বই খুব ভাল চলছে। আরও লেখার প্রেরণা দিচ্ছেন তিনি। হাসপাতাল থেকেই ব্লাড ব্যাংকের অকাজের সময়গুলোয় মিটফোর্ডের কাছেই বাংলাবাজারে গিয়েছি বইয়ের খবর নিতে, দুএকদিন যাওয়ার পর একদিন তাঁকে বলি, যে করেই হোক একটি বাড়ি যেন তিনি আমার জন্য খোঁজেন, ভাড়া নেব। ইতিমধ্যে হাসপাতালের আশে পাশে বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে মাথায় টু লেট লেখা যে বাড়িতেই গিয়েছি, বাড়ি, বাড়িভাড়া সবই পছন্দ হবার পর, বাড়িঅলা জিজ্ঞেস করেছেন, ‘কে কে থাকবে বাড়িতে?’
‘আমি থাকব।’
‘আপনি সে তো বুঝলাম, কিন্তু পুরুষ কে থাকবে আপনার সঙ্গে?’
‘কোনও পুরুষ থাকবে না, আমি একা থাকব।’
বাড়িঅলা চমকে উঠেছেন, ‘একা আবার কোনও মেয়েমানুষ কোনও বাড়িতে থাকে নাকি!
আপনার স্বামী নাই?’
‘না।’
‘না, কোনও একা মেয়েমানুষকে আমরা বাড়ি ভাড়া দিই না।’
মুখের ওপর দরজাগুলো ধরাম করে বন্ধ হয়ে যায়। তারপরও আশা ছেড়ে দিই না। খোকা রাজি হলে খোকাকে নিয়ে বেরোই বাড়ি দেখতে। যে বাড়িই পছন্দ হয়, সে বাড়িতেই, যেহেতু খোকা পুরুষ মানুষ, বাড়িঅলা তাঁকেই জিজ্ঞেস করেন, কে কে থাকবে বাড়িতে? খোকা বলেন, ‘উনি থাকবেন, উনি ডাক্তার, মিটফোর্ড হাসপাতালে চাকরি করেন।’
‘উনার স্বামী নাই?’
খোকা খুব নরম কণ্ঠে বলেন, ‘না, উনার স্বামী নাই। মিটফোর্ড হাসপাতালে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন। হাসপাতালের কাছাকাছি থাকলে সুবিধা। আপনারা ভাড়ার জন্য চিন্তা করবেন না। উনি যেহেতু ডাক্তারি চাকরি করেন, বুঝতেই তো পারছেন, মাস মাস বাড়িভাড়া দিতে উনার কোনও অসুবিধে হবে না।’
খোকাকে নিয়ে এসে এইটুকু অন্তত কাজ হয় একজন ডাক্তার যে বাড়িভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তা তিনি নিজমুখে ব্যাখ্যা করে বাড়িঅলাদের রাজি করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যতই মধুর কণ্ঠে মধুর হেসে বলা হোক না কেন, সত্যিকার কোনও কাজ হয় না। কেউই বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না কোনও একলা মেয়েমানুষকে। অত্যন্ত অমায়িক কিছু সজ্জন বাড়িঅলা পেয়েছি, যাঁরা মুখের ওপর ধরাম করে দরজা বন্ধ করে দেননি, বা যান ভাই রাস্তা মাপেন, বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাবে না বলে দূর দূর করে তাড়াননি, খোকার সবিশেষ অনুরোধে রাজি হয়েছেন বাড়ি ভাড়া দিতে তবে মেয়ের বাবা বা ভাইকে সঙ্গে থাকতে হবে। এর অর্থ স্বামী যদি না থাকে, কি আর করা যাবে, পোড়া কপাল মেয়ের, তবে কোনও একজন পুরুষ আত্মীয়ের থাকতেই হবে সঙ্গে। কেন একটি মেয়ের একা থাকা চলবে না তা বিশদ করে কেউ বলেন না। আমার অভিভাবক একজন কেউ থাকতেই হবে। আমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ, আমিই আমার অভিভাবক— এ কথা কেউ মানেন না। বাবা ভাই মামা কাকা কাউকেই যে সম্ভব নয় তাদের জীবন থেকে তুলে এনে আমার সঙ্গে রাখার, তা খোকাকে বলি। খানিক পর মার কথা মনে হয়, এক মাকেই আনা যেতে পারে। কিন্তু মা তো পুরুষ নন, বাড়িঅলারা পুরুষ চান। একজন ডাক্তার মেয়ের সঙ্গে যদি তার মা বাস করেন তবে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে কি না তার খোঁজও নেওয়া হল, এতেও লাভ হল না। খুঁজে খুঁজে ঘেমে নেয়ে রাস্তা মাপতে মাপতে আশা ছেড়ে দেওয়ার আগে শেষ চেষ্টা করে দেখার মত যে বাড়িটিতে ঢুকি সেটি আরমানিটোলার এই বাড়িটি। বাড়ির মালিকের সামনে খোকা যতটা বিনীত হতে পারেন হয়ে ঘন্টা দুয়েকের প্রশ্নোত্তরে পাশ মার্ক জুটিয়ে মা আর মেয়ের থাকার ব্যপারে অনুমতি লাভ করেন। জাহাজের মত এই বিশাল বাড়িটির মালিক একটি অশিক্ষিত লোক, লোহা লককরের ব্যবসা করে টাকার পাহাড় হয়েছেন। টাকার পাহাড় হলে যা করে বেশির ভাগ লোক, তিনি তাই করেছেন, দাড়ি রেখেছেন, মাথায় টুপি পরেছেন আর আল্লাহকে সাক্ষী রেখে চারটে বিয়ে করেছেন। চার বউকে পৃথক পৃথক চারটে বাড়িতে রেখেছেন। জাহাজ বাড়িটির দোতলায় চার নম্বর বউ নিয়ে বাস করেন। বাড়িভাড়া তিন হাজার, আর আমার মাইনে কচ্ছপের মত হেঁটে হেঁটে সাকুল্যে আড়াই হাজারে দাঁড়িয়েছে। এই পার্থক্য সত্ত্বেও বাড়ির পাঁচতলায় দুটো ঘর আর লম্বা টানা বারান্দার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিই। একা আমি নিজের বাড়িতে থাকব, অন্যের বাড়িতে অন্যের আদেশ মত নয়, এই আনন্দ এবং উত্তেজনায় আমি কাঁপি। জীবনের প্রথম কারও ওপর ভরসা না করে জীবন যাপন করার জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সস্তায় একটি খাট, সস্তায় তোশক বালিশ চাদর, একটি ইস্পাতের আলমারি আর কিছু প্রয়োজনীয় বাসন কোসন কিনে আপাতত বাড়িটি বাসযোগ্য করি। ময়মনসিংহ থেকে মাকে নিয়ে আসি, লিলিকেও। আলাদা একটি বাড়ি ভাড়া করে সম্পূর্ণ নিজের পছন্দ মত থাকায় মাও খুব খুশি। মা এসেই লিলিকে দিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করে গুছিয়ে রান্নাবান্না করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরমানিটোলার মাঠে ছেলেপেলেদের ফুটবল খেলা, রাস্তার গাড়িঘোড়া আর খোলা আকাশ দেখেন। ধীরে ধীরে জানালার পর্দা কিনি, বিস্তর দরদাম করে বড় একটি লাল সবুজ রঙের তকতির ডিজাইন করা লাল কার্পেট কিনি, রং মিলিয়ে কয়েকটি কুশনও। কোনও সোফা বা চেয়ার টেবিল কেনার টাকা নেই, তাই কুশনেই হেলান দিয়ে কোনও অতিথি এলে যেন বসতে পারে। সোফা যে কিনতে পারিনি, সে জন্য মনে কোনও দুঃখ থাকে না। নিজের প্রথম সংসারটি বড় সুন্দর করে সাজাতে ইচ্ছে করে, সুন্দর সুন্দর জিনিসের দিকে চোখ যায়, কিন্তু আমার সামর্থের বাইরে বলে সুন্দর থেকে চোখ ফিরিয়ে কম দাম কিন্তু দেখতে অসুন্দর নয়, তেমন জিনিস খুঁজি। তেমন জিনিসই নিজের উপার্জিত টাকায় কিনে নিজের সংসারে এনে যে আনন্দ হয় তার তুলনা হয় না। যে মাসে কার্পেট কেনা হয়, সেই মাসে অন্য কিছু কেনার জো থাকে না। পরের মাসের জন্য অপেক্ষা করি। এই অপেক্ষাতেও একধরনের সুখ আছে। মাইনের টাকায় বাড়িভাড়াই যেহেতু দেওয়া সম্ভব নয়, ভরসা লেখার ওপর। সাপ্তাহিক পূর্বাভাস আর পাক্ষিক অনন্যায় কলাম লিখি। খবরের কাগজ আর আজকের কাগজ থেকে নাইমের প্রভাব দূর হওয়ার পর ওসবেও লিখতে শুরু করি। বিদ্যাপ্রকাশ থেকে আরও একটি কবিতার বই বেরিয়েছে অতলে অন্তরীণ নামে। বই চলে ভাল। বই চললেও রয়্যালটির টাকা আমি দাবি করি না। লজ্জা হয় টাকা চাইতে তাছাড়া আমার স্বনির্ভর জীবনে খোকার আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে বড় কৃতজ্ঞ করে রেখেছে। বাজার করতে যাব, কোথায় বাজার দেখিয়ে দিচ্ছেন। আসবাবপত্র কিনতে যাবো, থাল বাসন কিনতে যাব, কোথায় যেতে হবে, নিয়ে যাচ্ছেন, দরদাম করে দিচ্ছেন। ডাল ভাত খাচ্ছি অনেকদিন, দেখে একদিন তিনি দুটো মুরগি কিনে নিয়ে এলেন। আমার টাকা ফুরিয়ে আসছে দেখলে মা ময়মনসিংহে চলে যাচ্ছেন, বাবার ভাণ্ডার থেকে নিয়ে বস্তা ভরে চাল ডাল আনাজপাতি নিয়ে বাসে করে চলে আসছেন ঢাকায়। আমার দারিদ্র আছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে আনন্দও আছে। আমার জীবনে আমি এত দরিদ্র অবস্থায় কাটাইনি, এবং এত আনন্দও এর আগে আমি পাইনি। ভাইএর মত, বন্ধুর মত খোকা আছেন পাশে। মা আছেন তাঁর উজাড় করে ভালবাসা নিয়ে। লিলিও খুশি অবকাশের গাধার খাটুনি থেকে এসে অল্প কাজ আর শুয়ে বসে অনেকটা আকাশের কাছাকাছি থাকার আনন্দে। আমার হিসেবের সংসার অথচ সুখে উপচে পড়া জীবন। হাসপাতালে গাইনি বিভাগে প্রচণ্ড ব্যস্ততা আমার। রোগিতে সয়লাব হয়ে যায় বিভাগটি। ময়মনসিংহের হাসপাতালে গাইনি বিভাগে ইন্টার্নশিপ করার সময় যেমন উত্তেজনা ছিল, যেমন দম ফেলাম সময় ছিল না, এখানেও তেমন। ডেলিভারি করাচ্ছি, এপিসিওটমি দিচ্ছি, এক্লাম্পসিয়ার রোগী ভাল করছি, রিটেইন্ড প্লাসেন্টা বের করছি, ফরসেপ ডেলিভারি করছি, কারও এক্ষুনি সিজারিয়ান, দৌড়োচ্ছি অপারেশন থিয়েটারে, ঝটপট মাস্ক গ্লবস পরে সিজারিয়ানে অ্যাসিস্ট করতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, আবার গাইনি আউটডোরেও রোগী দেখতে হচ্ছে, সারাদিনে শত শত রোগীর ভিড়, সময়ের চেয়ে বেশি সময় চলে যায় রোগীর চিকিৎসা করে। সারাদিন এসব কাজ করার পর আবার রাতেও ডিউটি পড়ছে। সারারাত জেগে কাজ করতে হচ্ছে। অল্প যেটুকু সময় হাতে থাকে নিজের জন্য, তখন কলাম লিখি। বাড়তি টাকা রোজগার না করলে বাড়িভাড়া দেওয়া যাবে না, উপোস করতে হবে। হাসপাতালের ইন্টার্নি ডাক্তাররা আমি জানি না কেন, আমার বেশ ভক্ত হয়ে পড়ে, অনেকটা বন্ধু-মত। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ফারাক থাকলেও এই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমার পরিচয় ওরা সকলেই জানে। আমাকে বলতে হয় না আমি কে। পরিচয় জানার অসুবিধে এই, আমি কাজ করলেও মনে করা হয় আমার মন বুঝি ডাক্তারিতে নেই, মন কবিতায়। আমি প্রেসক্রিপশান লিখতে থাকলে দূর থেকে দেখে কেউ ভেবে বসে আমি হয়ত প্রেসক্রিপশান লিখছি না, কলাম লিখছি। আমার বয়সী ডাক্তাররা এফসিপিএস পাশ করে অথবা পুরো পাশ না করলেও ফার্স্ট পার্ট পাশ করে এসে রেজিস্টার হয়ে বসেছে নয়ত সিএ, ক্লিনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্ট। এই বয়সে আমার মত কেবল মেডিকেল অফিসার হয়ে যারা কাজ করছে বিভিন্ন বিভাগে, তাদেরও এফসিপিএস পরীক্ষা দেওয়ার ধান্দা। আমারই কোনও ধান্দা নেই। মোটা মোটা বই নিয়ে বসে যাব, বছরের পর বছর কেটে যাবে বইয়ে ঝুঁকে থেকে, এর কোনও মানে হয়! দেখেছি দশ বছরেও অনেকের পাশ হয় না, অথচ বছর বছর ক্লান্তিহীন দিয়েই যাচ্ছে পরীক্ষা, ফেলই করছে প্রতিবছর। টাকাঅলা বাপ যাদের তারা পিজির এফসিপিএস এ ফেল করে লণ্ডনে গিয়ে কোনও রকম ফেল টেল ছাড়াই এফআরসিএস ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরত আসে। বাংলাদেশের এফসিপিএস পাশ করার চেয়ে বিলেতের এফআরসিএস পাশ করা সহজ, এ কথা বিশ্বাস না হলেও কথা সত্য। এসব দেখে ইচ্ছে উবে গেছে। মিটফোর্ড হাসপাতালে চাকরি করছে এরকম যে ডাক্তারকেই দেখি আমার কাছাকাছি বয়সী, সকলেই চাকরি করার পাশাপাশি এফসিপিএসএর পড়াশোনা করছে। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে, আমি পরীক্ষা দিচ্ছি কি না। আমি সোজা না বলে দিই। অবাক হয় হবু এফসিপিএসরা। হাসপাতালে বসে তাহলে কি ঘোড়ার ডিম করছি, মনে মনে বলে তারা। খানিক পর হেসে, আবার মনে মনেই বলে, কদিন পর তো ঘাড় ধরে বের করে দেবে পোস্টিং দিয়ে কোনও গাঁও গেরামে। শহরের বড় হাসপাতালে চাকরি করতে আসবে যারা পড়াশোনা করছে, এফসিপিএসের মাঝপথে অথবা শেষের পথে। তা ঠিক, হবু এফসিপিএসরা পড়ার ঘোরেই থাকে, তাদের কাজে কোনও অনিয়ম হলে কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু আমার মত ছোট ডাক্তারদের ওপর ইন্টার্নি ডাক্তারদের মত খাটনি যায়। আমার আপত্তি নেই খাটনিতে। কিন্তু কবি বলে নাম থাকায় আমাকে উদাসীন বলে মনে করা হলে আমার বড় মন খারাপ হয়। আর কেউ উদাসীন না বললেও প্রফেসর রাশিদা বেগম বলেন। তিনি আমাকে প্রথম দিন থেকেই মোটেও পছন্দ করতে পারছেন না। প্রথম দিন বিভাগে যেতে আমার দু মিনিট দেরি হয়েছিল বলে। রাশিদা বেগমের মাথার কোষে কোষে গেঁথে গেছে সেই দুমিনিটের কাহিনী। এমনিতে খিটখিটে মেজাজ তাঁর। গাইনি বিভাগের তিনটি শাখার মধ্যে তিন নম্বর শাখার তিনি অধ্যাপিকা। ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মত মহাশয়ার অবস্থা। মেজাজ ছাড়া তাঁর বিশেষ কিছু সম্পদ নেই। রোগী সামলাতে নাস্তানাবুদ হন, কারও গোচরে এলে তিনি অবস্থা সামাল দিতে চোখের সামনে যাকেই পান তাঁর ওপর চোট দেখান, এতে যেন তাঁর গলার স্বর সকলে শোনে এবং তাঁকেও যেন খানিকটা মান্যগন্য করে তাঁর সহকারীরা, যেমন করে বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বায়েস ভুইয়াকে। বায়েস ভুঁইয়া চমৎকার মানুষ। তাঁর কাউকে ধমক দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁর কাজই তাঁর মূল্য নির্ধারণ করে। দেখা হলেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেমন আছি, ইতিবাচক উত্তর ছুঁড়ে দিয়ে খুব দ্রুত সরে যাই তাঁর সামনে থেকে। প্রথমত আমার একটু কুণ্ঠাও থাকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছি না বলে। অধ্যাপকের আশে পাশে যারাই ভিড় করে থাকেন, সকলেই পোস্ট গ্রাজুয়েশনের অর্ধেক নয়ত পুরো ডিগ্রি নিয়েছে। আমি তাই সংকোচে দূরে থাকি। এই সংকোচই আমার ইচ্ছের অংকুরোদগম ঘটায় মনে, এফসিপিএসএর জন্য লেখাপড়া শুরুই না হয় করে দিই। মাও বলেন, বিসমিল্লাহ বইলা শুরু কইরা দেও, তোমার বাপও খুশি হইব। বায়েস ভুঁইয়া বিভাগের অধ্যাপক হয়েও আমাকে বেশ খাতির করেন, কারণটি আমার ডাক্তারি বিদ্যে নয়, আমার লেখা। পত্রিকায় আমার লেখা পড়েন তিনি। মাঝে মধ্যে আমাকে ডেকে আমার এই লেখাটি কিংবা ওই লেখাটি তাঁর খুব ভাল লেগেছে বলেন। লেখালেখির বিষয়টি হাসপাতালের চৌহদ্দিতে উঠলে আমার বড় অস্বস্তি হয়। তবু ওঠে। হাসপাতালে আমি যে কোনও ডাক্তারের মত ডাক্তার। আমার অন্য পরিচয়টি হাসপাতালে এসে আমার হাসপাতালের পরিচয়টি সামান্যও গৌণ করবে তা আমার মোটেও পছন্দ নয়। অ্যপ্রোন পরে হাতে স্টেথোসকোপ নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি, দেখে মা খুব খুশি হন। আমাকে মুখে তুলে খাওয়ান। আমার পরিচর্যা করতে মা সদাসর্বদা ব্যস্ত। টাকা জমিয়ে একদিন স্টেডিয়াম মার্কেট থেকে ছোট একটি লাল রঙের রেফ্রিজারেটর কিনে আসি। ফ্রিজটি মা দিনে দুবেলা পরিষ্কার করেন নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে। লিলিকে হাত দিতে দেন না ফ্রিজে, কিছু যদি কোথাও দাগ লাগিয়ে ফেলে লিলি। বাইরে থেকে গরমে সেদ্ধ হয়ে এলে মা দৌড়ে এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি এনে দেন। রান্না করে করে ফ্রিজে রেখে দেন যেন অনেকদিন খেতে পারি, যেন বাজার করতে না হয় ঘন ঘন। আমাদের সুখের সংসার অভাবে আনন্দে চমৎকার কাটতে থাকে। ইন্টার্নি ডাক্তাররা বেড়াতে আসে বাড়িতে, খেয়ে দেয়ে হল্লা করে ডাক্তারি ভাষায় আড্ডা পিটিয়ে চলে যায়। আমার এই একার সংসারটি সকলের বেশ পছন্দ হয়। খাওয়া দাওয়া প্রথম প্রথম কার্পেটে বসেই হত, এরপর বাড়িতে অতিথির আগমন ঘটতে থাকায় ছোট একটি টেবিল আর দুটো চেয়ার রান্নাঘরে বসিয়ে দিই। ছোট একটি টেলিভিশন, ছোট একটি গান শোনার যন্ত্রও কিনি। আর কিছুর কি দরকার আছে? মা বলেন, না নেই। মা আমাকে বাধা দেন টাকা খরচ করতে। টেবিল চেয়ার গুলো যদি অবকাশ থেকে আনা যেত, তিনি খুশি হতেন। বাপের সম্পদে তো মেয়েরও ভাগ আছে। অথচ বাপ তো কোনওরকম সাহায্য করছে না, মা গজগজ করেন। বাপ সাহায্য না করলেও বাপের প্রতি ভালবাসা আমাকে বায়তুল মোকাররমের ফুটপাত থেকে হলেও বাপের জন্য সার্ট কেনায়, জুতো কেনায় ময়মনসিংহে যাওয়ার আগে। ছুটিছাটায় দুএকদিনের জন্য ময়মনসিংহে যাওয়া হয়। বাপকে দেখতেই যাওয়া হয়। বাপের কোনও সাহায্য নিতে আমার ইচ্ছে করে না বরং বাপকে সাহায্য করতে ইচ্ছে হয়। সাধ আছে অনেক, সংগতি তত নেই। সংগতি বাড়াতে সাইনবোর্ড টাঙিয়েছি আরমানিটোলার বাড়ির সদর দরজায়। ডাক্তার তসলিমা নাসরিন, এম বি বি এস। রোগী দেখার সময় এতটা থেকে এতটা। মাইনের টাকা, রোগী দেখার টাকা, লেখালেখির টাকা সব মিলিয়ে যা হয় তা পই পই হিসেব করে ইস্পাতের আলমারিতে রাখি। বাপের সার্ট জুতো এসব হিসেবের বাইরে। হোক না! বাড়তি খরচের জন্য শাক ভাত খেতে হয়। না হয় খেলামই।
ময়মনসিংহের আত্মীয় স্বজন ঢাকায় কোনও কাজে এলে আমার বাড়িতে ওঠে। দেখে আমার খুব ভাল লাগে। ছটকু এল একবার। কার্পেটে শুল। তাতে কী! ভালবাসা থাকলে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়েও সুখ। ছটকু নিজেই বলেছে যে বড় মামা, ফকরুল মামা, ঝুনু খালা বা ছোটদার বাড়িতে গিয়ে এ যাবৎ কোনও স্বস্তি পায়নি, পেয়েছে আমার বাড়িতে এসেই, ছোট হোক বাড়ি, এটা না থাক, ওটা না থাক, কিন্তু নিজের মত পা ছড়িয়ে বসা যায়, গলা ছেড়ে গান গাওয়া যায়, কিছু খেতে ইচ্ছে করলে চেয়ে খাওয়া যায়। মনে হয় নিজের বাড়ি, এমন।
কেবল যে গাইনি বিভাগের ব্যস্ততায় আর পত্রিকার জন্য কলাম লিখেই সময় পার করি তা নয়। মাঝে মধ্যে সাহিত্যের আড্ডায় অনুষ্ঠানেও যাই। ময়মনসিংহের জাকারিয়া স্বপন, ইয়াসমিনের পাতানো ভাই, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, অনুষ্ঠানের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারক হতে আমাকে একদিন নিয়ে গেল। এর আগে আমাকে যা-ই হতে হয়েছে, কোথাও বিচারক হতে হয়নি। বিচারকদের যে গাম্ভীর্য থাকে, তা যথাসম্ভব ধারণ করে বিচার করে আসি বিতর্কের। একবার ফরহাদ মজহার আমন্ত্রণ জানালেন তার এনজিও উবিনিগে, উবিনিগের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের টাকা সাহায্য জোটে মজহারের অথচ নিজে তিনি এককালের সমাজতান্ত্রিক। টিএসসিতে তাঁর গান শুনেছিলাম অনেক আগে, নিজে গান লিখতেন, সুর দিতেন, গাইতেনও। নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে ঘর ভরা দর্শককে যতগুলো গান শুনিয়েছিলেন তার মধ্যে সাততাড়াতাড়ি যাচ্ছি বাড়ি গানটি বেশ লেগেছিল। বামপন্থী গায়কটি গান টান ছেড়ে দিয়ে নিজের কবিতার বই বের করলেন। চমৎকার সব কবিতা লিখেছেন। পড়ে মুগ্ধতার শেষ নেই আমার। যাই হোক, তাঁর খবর পেয়ে সাততাড়াতাড়ি তাঁর আপিসে গিয়ে দেখা করি। একটি হাড়গিলে মহিলা নাম ফরিদা আখতার উঠে এলেন ফরহাদ মজহারের ঘর থেকে, মনে হল যেন শয্যা থেকে উঠে এলেন। আমাকে বসিয়ে ভেতর ঘরে ডাকতে গেলেন তাঁকে। ভেতর থেকে বেরোতে অনেকটা সময় নিল তাঁর। মনে হল শয্যা থেকে উঠে উদোম গায়ে সবে কাপড় চড়িয়ে এলেন। চা বিস্কুট এল। কথা চলল। কথা চলল, আসলে তিনি একাই কথা বললেন। তাঁর নিজের কবিতার কথা বললেন, কবিতার কিছু আরবি শব্দ আমি বুঝতে পারিনি বলে তিনি আরবির অর্থ বলে দিলেন। অবোধ্য আরবি শব্দ কবিতায় ব্যবহার করার কি কারণ এই প্রশ্ন করার আগেই তিনি বললেন, এ দেশের বাংলা হচ্ছে ইসলামি বাংলা, আর পশ্চিমবঙ্গের বাংলা হিন্দু বাংলা। আমাদের সংস্কৃতি ইসলামি সংস্কৃতি, আমাদের ভাষায় প্রচুর আরবি উর্দু শব্দ মেশানো উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। ধাঁধা লাগে শুনে। তিনি কি আমাকে দলে টানতে চাইছেন তাঁর এই উদ্ভট মিশনে! তা না হলে আমাকে এমন তলব করার কারণ কি! আসলেই তিনি আমাকে দলে টানতে চাইছেন। এসব আজগুবি চিন্তা নিয়ে তিনি চিন্তা নামে একটি পত্রিকা বের করবেন, ওতে যেন লিখি আমি। ফরহাদ মজহার সম্পূর্ণই পাল্টো গেছেন। এই দেশে ইসলামি মৌলবাদ যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, গুটিকয় মানুষ এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, গুটিকয় মানুষ চাইছে বাঙালি সংস্কৃতি যে সংস্কৃতি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকলের সংস্কৃতি, তাকে সবলে অস্বীকার করছেন মজহার। দেশ বিভাগের ভূল সিদ্ধান্ত বাংলাকে বিভক্ত করেছে, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিতে মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই, সে যে কোনও সুস্থ মানুষই জানে। কিন্তু ফরহাদ মজহারের মত চিন্তাবিদের এ কী হাল, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস থেকে ফট করে পুঁজিবাদীদের টাকায় এনজিও খুলেছেন, এখন আবার গাইছেন ধর্মের গান! কোনও এক ফকিরের গানও শোনালেন আহা কি মধুর বলতে বলতে, দীনের নবী মোস্তফা.. হরিণ একটা বান্ধা ছিল গাছেরই তলায়। আরব দেশের মরুভূমিতে গাছও নেই, হরিণও নেই, অথচ নাকি কী অভাবনীয় কল্পনার মিশ্রণ এই গানটিতে! এই গানকেই তিনি বাংলাদেশের গান বলছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত হিন্দু দের গান, মুসলমানদের গান নয়। বলে দিলেন। ফরহাদ মজহারের এই মতের বিরুদ্ধে পরে আমি একটি কলাম লিখি পত্রিকায়, সঙ্গে শামসুর রাহমানের কবিতায় উর্দূ শব্দ ব্যবহার আর হুমায়ুন আজাদের রবীন্দ্রনাথ বিরোধী বক্তব্যেরও প্রতিবাদ ছিল আমার কলামে। দীর্ঘদিন আমার ওই ভাষা নিয়ে লেখাটির সূত্র ধরে পত্রিকায় লেখালেখি চলল। ফরহাদ মজহার নিজে লিখলেন। তাঁর যুক্তি এবং ইনকিলাব পত্রিকার ছাপা হওয়া কোনও মৌলবাদির যুক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে আরও অনেকে কলাম লিখলেন। পূরবী বসু আমেরিকার পাট চুকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছেন, তিনি এসেই কলম ধরলেন ফরহাদ মজহারের মতের বিপক্ষে। লোকটির চরিত্র ক্রমশ সন্দেহজনক হয়ে উঠছে, তা স্বীকারও করলেন অনেকে।
ভাষা নিয়ে আমার লেখাটি ছাপা হওয়ার পর শামসুর রাহমান বড় একটি কলাম লিখলেন আমার কলামের উত্তরে। তসলিমাকে তসলিম জানিয়ে তিনি শুরু করেছেন। লিখেছেন আত্মপক্ষ সমর্থন করে। আমি, এটা ঠিক, যে, বাংলা ভাষায় আরবি ফার্সি, উর্দূর অনধিকার প্রবেশ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে শামসুর রাহমানকে দোষারোপ করেছি তিনি উর্দু শব্দ ব্যবহার করেন বলে। যে শব্দগুলো বাংলা অভিধানে আছে, তার ওপর প্রচলিত, কী দরকার সেই শব্দগুলো ব্যবহার না করে সে ক্ষেত্রে উর্দু শব্দ ব্যবহার করার! শামসুর রাহমান লিখেছেন, ‘প্রত্যেক ভাষাতেই অতিথি শব্দের সমাবেশ ঘটে। অতিথির মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া আতিথেয়তার রীতিবিরুদ্ধ কাজ। দরজা খোলা রাখা দরকার, সব অতিথিই যে বাঞ্ছিত ও কাঙ্খিত হবে, এটা বলা যাবে না। অবাঞ্ছিত অতিথি অনাদরে নিজে থেকেই কেটে পড়বে। ..অন্নদাশংকর রায় কিন্তু বেশ কিছু উর্দু ও হিন্দি শব্দ অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেন। আমার কাছে কখনো দুর্বোধ্য কিংবা শ্রুতিকটু মনে হয়নি। তিনি এক জায়গায় জান পেহচান ব্যবহার করেছেন চেনাজানার বদলে। তাঁর একটি বাক্য উদ্বৃতি করছি, কমলি নেহি ছোড়তি। তসলিমা নাসরিন, আমি কিন্তু এতদূর যাইনি। তাহলে কি আপনি বলবেন শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকর রায় পশ্চিমবঙ্গে বসে ইসলামি বাংলা ভাষা তৈরি করছেন?’ আমি যে লিখেছিলাম ভাষাকে নতুনত্ব দেবার বা সমৃদ্ধ করবার জন্যে এই বাংলা ভাষা এত ভিখিরি হয়ে যায়নি যে অন্য ভাষা থেকে শব্দ হরণ করবার বা ধার করবার কোনো দরকার আছে। আমাদের যা আছে তা নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকি না কেন! বরং শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবার চেয়ে সাহিত্যকে গুণগত সমৃদ্ধি দেবার আগ্রহ থাকা উচিত সকল সৎ সাহিত্যিকের। .. এ কথার উত্তরে তিনি লিখেছেন, ‘না, তসলিমা, এই উক্তি আপনার মত প্রগতিশীল ব্যক্তির যোগ্য হয়নি। আমাদের সমাজ একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বলেই কি তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাদের? এর পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টাশীল হতে হবে না? বাইরের দুনিয়ার ভালো ভালো জিনিস কি আমরা আমদানি করবো না সমাজ বদলের জন্যে? কোনো ভাষাই, সে ভাষা যত উন্নত ও ধনীই হোক, শব্দঋণ বিষয়ে লাজুক কিংবা নিশ্চেষ্ট নয়, এ কথা নিশ্চয় আপনার জানা আছে।’ আমার জানা আগে না থাকলেও জানা হয়। শামসুর রাহমান আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। তিনি বাঙালির ভাষার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের ভাগ আনেন না। তিনি একশ ভাগ অসাম্প্রদায়িক মানুষ। ফরহাদ মজহারের মত ইসলামি বাংলা কায়েম করতে চান না। আমি নতুন করে ভাবতে বসি, ভেবে আমি তাঁর সঙ্গেই একমত হই, নিজের ভুলগুলো স্পষ্ট হয়। আসলে সত্যি কথা বলতে, ইসলামি ভাষা বলে কোনও ভাষা নেই। ভাষার কোনও ধর্ম নেই। আরবি ভাষাকেই বা ইসলামি ভাষা বলব কেন! আরবি ভাষার লোক নানা রকম ধর্মে বিশ্বাস করে, তারওপর ওদের মধ্যে এমন লোকও প্রচুর, যারা কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করে না। ভাষা আপন গতিতে চলবে, চলেছে, ভাষাকে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক নয়। আসলে, ইসলামি ভাষা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার আমার কারণ ছিল একটিই, ইসলামপন্থী লোকেরা এ দেশটিকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে, লোকগুলো একসময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল, এখন এই স্বাধীন বাংলায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে জোর জবরদস্তি করে ইসলামি বাংলা বানানোর ষড়যন্ত্র করছে— এই আশঙ্কা থেকেই তথাকথিত ইসলামি ভাষাকে রোধ করতে চেয়েছিলাম। মুশকিল কিছু ধর্মান্ধ লোক নিয়ে। কিছু মন্দ লোক মন্দ উদ্দেশে ভাষাকে খৎনা করে ভাবছে ইসলামি পতাকা ওড়াবে দেশে। কেবল ভাষাতেই তো নয়, রাজনীতির মগজেও গাদা গাদা ইসলাম ঢোকানো হচ্ছে। যদি দেশটি শেষপর্যন্ত ইসলামি শাসনে চলে, তবে আর ভাষা থেকে আরবি ফার্সি উর্দু বিদেয় হলেই বা কী! আমার দুশ্চিন্তা দূর হয় না।
কী এমন আর কলাম লিখি! কী এমন ভাল! সাহিত্যের কতটুকুই বা আমি জানি! বাংলা সাহিত্যে লেখাপড়া করার ইচ্ছে ছিল, বাবা তো ঘাড় ধরে মেডিকেলে ঠেলেছেন। এতটা জীবন ডাক্তারি বিদ্যা ঘেঁটে সাহিত্যের কিছুই নিশ্চয়ই শেখা হয় নি আমার। কবিতা লেখার অভ্যেস না হয় আছে, কিন্তু সেই অভ্যেস থেকে গদ্যে হাত পড়লে আদৌ কিছু রচিত হয় বলে আমার মনে হয় না। যা রচিত হয়, তা আলোচিত হলেও প্রশংসিত হলেও আমার সংশয় যায় না। খুঁতখুঁতি থেকেই যায়। তবে গদ্য পদ্য যা কিছুই লিখি না কেন, সবই হৃদয় থেকে আসে। লোকে যেন পড়ে বাহবা দেয়, যেন খুশি হয়, বানিয়ে বানিয়ে এমন কিছু, এমন কিছু যা আমাকে ভাবায় না, যা আমাকে কাঁদায় না, আমার ভাবনার নির্যাসটুকু নিংড়ে আনে না, আমার দ্বারা লেখা হয় না। খোকা একদিন বললেন, আমার কলামগুলো জড়ো করে একটি বই প্রকাশ করবেন তিনি। শুনে অবাক হই! পত্রিকার এসব কলাম কি সাহিত্য নাকি যে তিনি বই করতে চাইছেন! লজ্জায় মরি! বলি, ‘বলছেন কি! এসব তো প্রতিদিনকার অনুভব নিয়ে, খবর নিয়ে! কি হয়েছে গতকাল, কি হচ্ছে আজ এসব নিয়ে! কদিন পরই এসব সাময়িক ঘটনার ওপর লেখাগুলোর কোনও গুরুত্ব থাকবে না।’ খোকা মাথা নাড়েন, বলেন, ‘তা হোক না, সবই কি আর একরকম! কিছু কিছু তো আবার সবসময়ের জন্য চলে।’ আমি হাতের কাছে যে কটি পত্রিকায় আমার কলাম পেয়েছি, দেখিয়ে পড়িয়ে প্রমাণ দিয়ে বলি যে চলে না। মন কিছুতেই সায় দেয় না এই ভাষায় দুর্বল এমনকী বিষয়ে দুর্বল কলামগুলো নিয়ে কোনও বই করতে। খোকাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি, বলি যে বই যদি ছাপতেই চান, তবে কবিতার বই লিখে দিচ্ছি, সেটা ছাপুন। দৈনিক সাপ্তাহিকীর তুচ্ছ বিষয়বস্তু নিয়ে বই করার দুঃসাহস অনুগ্রহ করে দেখাবেন না। আরও একটি বৈষয়িক কারণ দেখাই, কলামের বই কেউ কিনবে না, কারণ সবারই কলামগুলো পড়া হয়ে গেছে। কিন্তু খোকার ইচ্ছে এতই তীব্র যে তিনি পুরোনো পত্রিকা ঘেঁটে ঘেঁটে জড়ো করতে থাকেন কলাম। কী নাম দেওয়া যায় বইএর, তিনি আমার কাছে জিজ্ঞেস করেছেন। কোনও নামই আমার মাথায় আসে না। ভোঁতা মাথার সঙ্গে একদিন শাহরিয়ারের দেখা। বইয়ের নামের প্রসঙ্গ উঠতেই শাহরিয়ার বলল, নির্বাচিত কলাম। নির্বাচিত কলাম? এ কোনও নাম হল? কলাম তো পত্রিকার লেখা, বইএ চলে গেলে কোনও লেখাকে তো আর কলাম বলা যায় না, নিবন্ধ বা প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। আমি যুক্তি দেখাই। কিন্তু আমার এসব কলামকে নিবন্ধ বা প্রবন্ধ বলতেও সাহস হয় না। ওগুলোকে অনেক তথ্যভিত্তিক হতে হয়, রীতিমত গবেষণা করে লিখতে হয়। আমার কলামগুলো হালকা, মোটেও ভারী কিছু নয়, এসব আর যা কিছুই হোক কোনও নিবন্ধ বা প্রবন্ধ হয়নি। শেষ পর্যন্ত শাহরিয়ারের কথাই রইল। নির্বাচিত কলাম নামটিই পছন্দ করেন খোকা। লেখাগুলো কলাম হিসেবে পরিচিত হওয়ার কারণেই সম্ভবত তিনি সরাসরি বইয়ের নামে কলাম শব্দটি ব্যবহার করতে চাইলেন। আমি আগ্রহ না দেখালেও খোকা বই বের করলেন। বই হু হু করে চলল, এক মেলাতেই সব বই শেষ হয়ে আবার নতুন মুদ্রণ এল। খোকার মুখ থেকে হাসি সরে না। বইমেলায় বইয়ের বিক্রি দেখে খোকা তো খুশি, আবার বিস্মিতও। তিনিও ভাবেননি, কলামের বইটি এত বিক্রি হবে। আমাকে তাঁর স্টলে বসতে অনুরোধ করেন। বসলে লোকে অটোগ্রাফ নিয়ে বই কেনে। কবিতার বইও দেদার বিক্রি হচ্ছে, মেলাতেই বই বিক্রি সব হয়ে যায়, বই আবার ছেপে আনেন খোকা। কোনও কবিতার বই এরকম বিক্রি হয় না তিনি বলেন। ঢাকার মানুষ তো আছেই, ঢাকার বাইরে থেকেও মানুষ আসে আমাকে এক নজর দেখতে, আমার সই করা বই কেনার জন্য রীতিমত ভিড় জমে যায়। সব কেমন অদ্ভুত লাগে। অবিশ্বাস্য লাগে।
হাসপাতালে ডিউটি না থাকলে অথবা কোনও বিকেলে হঠাৎ হঠাৎ অবসর পেলে সাহিত্যিক যে আড্ডায় আমার যাওয়া হয় সে নীলক্ষেতে অসীম সাহার ইত্যাদির আড্ডা। ওখানেই এক বিকেলে রুদ্রর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাই। দুজনেরই কত না বলা কথা জমে আছে। সেই কতদিন থেকে আমরা আমাদের চিনি, অথচ জানি না কে কেমন আছে। কারও জীবন যাপনের কিছু আমাদের জানা নেই। আড্ডা থেকে উঠে আসার আগে জিজ্ঞেস করি, যাবে আমার সঙ্গে? কোথায় যাব, কি হবে কিছুই না জিজ্ঞেস করে রুদ্র বলে, যাবো। রিক্সা নিয়ে আরমানিটোলার দিকে যাই। পথে রুদ্র আমাকে বলে যে তার চিংড়ির ব্যবসা সে গুটিয়ে নিয়েছে। মিঠেখালিতে বহুদিন ছিল। কবিতা লিখছে, নতুন একটি গান লিখেছে। গানটি সে রিক্সাতেই গেয়ে শোনায়, ভাল আছি, ভাল থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো। হৃদয় স্পর্শ করে গানের প্রতিটি শব্দ। রুদ্রকে নিয়ে আরমানিটোলার বাড়িতে ঢোকার পর সেই বিকেলেই নাইম দরজার কড়া নেড়েছিল।
রুদ্র চোখ মেলে দেখে আমার সুখের সংসারটিকে।
‘কেমন দেখছো আমার সংসার!’ অহংকার আমার গ্রীবায় এসে বসে যখন বলি। রুদ্র বলে, ‘তুমি পারোও বটে।’
‘পারবো না কেন! ইচ্ছে থাকলেই হয়! অনেক আগেই এই ইচ্ছেটি করা উচিত ছিল আমার। নিজের বাড়ি। নিজের টাকা। কেউ নাক গলাবার নেই। কেউ আদেশ দেবার নেই। কি করছি না করছি তা নিয়ে কাউকে কৈফিয়ত দেবার নেই। এর চেয়ে সুখ আর কী আছে, বল!’
সন্ধের পর রুদ্র তখনও ঘরে, মিনার আসে একটি প্রস্তাব নিয়ে, একটি গাড়ি যোগাড় করে ময়মনসিংহে যাচ্ছে সে, যদি আমি যেতে চাই, যেতে পারি। মিনার গল্প লিখত একসময়, এখন বিচিন্তা নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাপে। জানি না কোত্থেকে আমি কোথায় চাকরি করছি তার খবর নিয়ে একদিন টেলিফোন করেছিল হাসপাতালে। গভীর রাতে ফোন করেছে কদিন, নাইট ডিউটিতে তখন রোগী নেই, রোগী না থাকলেও ডিউটির ডাক্তারদের ঘুমোনো ঝিমোনো সব নিষেধ, অগত্যা বসে বসে কথা বলেছি। কথা বলতে ভালও লেগেছে। মিনার সমাজ রাজনীতি এসব নিয়ে কোনও আলোচনায় যায় না।। কেবল হাসির কথা বলে। হাসির গল্প বলে একটি বই আছে, সম্ভবত মিনারের তা মুখস্ত। দেখা করতে এক বিকেলে এসেওছিল আরমানিটোলার বাড়িতে। বলল বহুদিন সে বিদেশে ছিল, বা্রজিলে চলে গিয়েছিল পালিয়ে। তার সেই পাগল করা সুন্দরী স্ত্রী কবিতার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এখন সে থাকে ইস্কাটনে। সেই মোহাম্মদ আলী মিনার নাম পাল্টো এখন মিনার মাহমুদ, চেকনাই বেড়েছে। গালে মুখে মাংশ, ত্বক আগের চেয়ে উজ্জ্বল।
‘বহু বছর পর দেখা। কেমন আছেন?’
কার্পেটের ওপর বসে চা খেতে খেতে মিনার বলে, ‘হ্যাঁ বহু বছর। আমি তো বেশ ভালই আছি। আপনার এই আস্তানাটি বেশ ভাল বানিয়েছেন তো!’
ঘরটিতে চোখ বুলোই। হ্যাঁ বেশ বানিয়েছি। বাবুই আর চড়ুই পাখির সেই কবিতাটি মনে পড়েছে । বাবুই গর্ব করে বলছে যেমনই তার বাসা হোক সে তো পরের বাসায় থাকছে না, থাকছে নিজের বাসায়।
কবিতা আর মিনারের ছাড়াছাড়ির খবরটি আমার মন খারাপ করে দেয়। তারুণ্যের তেজি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দুজনে উল্টো হাওয়ায় ছুটছে দেখতে ভাল লাগত। কেন ছাড়াছাড়ি হল, সমস্যা হলে মীমাংসার তো পথ আছে, কেন মিনার সেটির চেষ্টা করছে না, ইত্যাদি প্রশ্ন করলে খেয়ালি উত্তর জোটে।
‘ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে ফেলে কবিতাকে নিয়ে আবার জীবন শুরু করেন।’ পরামর্শ দিই। আমার পরামর্শ মিনার কতটুকু গ্রহণ করে তা বুঝতে পারি না।
মিনারের ময়মনসিংহের প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে যাই, রুদ্রকে জিজ্ঞেস করলে সেও রাজি। রুদ্র আর মিনারেরও দেখা হল বহুকাল পর। দু বন্ধু গাড়ির সামনে বসে। পেছনে আমি, পেছনে একসময় ঝুনুখালাও যোগ হয়, উঠিয়ে নিয়েছি ভূতের গলি থেকে। রুদ্রর সঙ্গে ঝুনুখালারও অনেকদিন পর দেখা হয়। রুদ্রর ইচ্ছে ময়মনসিংহে পৌঁছে একবার ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা করার। গাড়ি জয়দেবপুর পার হয়, ভালুকা পার হয়, ত্রিশাল পার হয়ে গাড়ির চাকা পিছলে রাস্তার মধ্যে উল্টো পাল্টা চককর থেয়ে একেবারে খাদে, না, ঠিক খাদে পড়তে গিয়েই কি কারণে জানি না, খাদের ঠিক কিনারটিতে আটকে যায়। ভেতরে মুত্যর সঙ্গে সকলের একটি সশব্দ মোলাকাত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা হয়ে থাকি গাড়ির সবাই। ঝুনু খালাকে নানির বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অবকাশের কালো ফটক দেখি ভেতর থেকে তালা দেওয়া, রাত তখন অনেক, এত রাতে ডাকাডাকি করে বাবাকে ঘুম থেকে তুলে তালা খুলিয়ে অবকাশে ঢোকার সাহস হয় না। বাবা আবার এত রাতে কী করে এলাম, কার সঙ্গে এলাম এসব জিজ্ঞেস করে পাগল করে ছাড়বেন, বিশেষ করে গাড়িতে বসা রুদ্রকে যদি চোখে পড়ে, তবে আর আস্ত রাখবেন না। অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে ইয়াসমিনের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ওর ঘরে রাতটুকু পার করে সকালবেলায় অবকাশে যাই। সারাদিন অবকাশে কাটে। সন্ধের পর অবকাশের সামনে গাড়ি এসে থামে, কথা ছিল ঢাকায় ফেরার পথে আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার। গাড়িতে উঠতে গেলে রুদ্র বলে, আমি ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা করব। ইয়াসমিন অবকাশেই ছিল। ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলি, ‘রুদ্র আইছে। তর সাথে দেখা করতে চাইতাছে।’
ইয়াসমিন বলে, কেন?
‘কেন মানে? গেটের কাছে দাঁড়াইয়া রইছে। যা, দেখা কইরা আয়।’
‘না।’
‘না কস কেন। কথা কইলে তর ক্ষতি কি?’
‘না আমি যাব না।’
‘আশ্চর্য! ঢাকা থেইকা আইছে, বার বার বলতে বলতে যে ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা করব। আর তুই দেখা করবি না? এত কাছে দাঁড়াইয়া রইছে। একটু কথা কইয়াই যাইব গা। তর অসুবিধাডা কি?’
ইয়াসমিনকে ঠেলেও পাঠাতে পারি না। রুদ্রকে গিয়ে বলি, ‘ইয়াসমিন আসছে না।’
‘আসছে না? বলেছো যে আমি দেখা করতে চাইছি?’
‘বলেছি। তবু আসছে না।’
রুদ্রর মন খারাপ হয়ে যায়। রুদ্রর এই মন খারাপ করা আমাকে কষ্ট দেয়। ইয়াসমিন যে রুদ্রর অনুরোধ ফিরিয়ে দিল তা না বলে আমি হয়ত বলতে পারতাম, ইয়াসমিন এ বাড়িতে নেই বা কিছু। ও এ বাড়িতে নেই, থাকলে দেখা করতে পারত বললে রুদ্রর মন নিশ্চয়ই খারাপ হত না। ফেরার পথে আমাদের খুব বেশি কথা হয়নি। রুদ্র জানালা খুলে বমি করে দুবার। ময়মনসিংহে বসে দুজনেই নাকি পেট ভরে মদ খেয়েছে। মিনার আমাকে আর রুদ্রকে আরমানিটোলায় নামিয়ে দিয়ে চলে যায় যেখানে যাবার।
রুদ্রকে আমিই বলি সে রাতে আমার বাড়িতে থেকে যেতে। আমার বিছানাতেই আমি তাকে শুতে দিই। এক হাতে যখন আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে, আমি তার হাতটিকে দিই জড়িয়ে ধরতে। যখন সে মুখটি এগিয়ে আনে আমার মুখের দিকে, চুমু খেতে চায়, দিই চুমু খেতে। যখন সে আমাকে আরও কাছে টেনে নিতে চায়, দিই নিজেকে তার আরও কাছে। যখন সে একটু একটু করে আরও ঘনিষ্ঠ হতে চায়, দিই তাকে ঘনিষ্ঠ হতে। যেন সেই আগের রুদ্র, আমি সেই আগের আমি। যেন মাঝখানে বিচ্ছেদ বলে কিছু নেই, কিছু ছিল না। যেন আগের মত আমাদের প্রতিদিন দেখা হচ্ছে। প্রতিদিন আমরা হৃদয় মেলাচ্ছি, শরীর মেলাচ্ছি। রুদ্রর উষ্ণ নিঃশ্বাস, খানিকটা জ্বরজ্বর গা আমার অনেকদিনের শীতল শরীরে উত্তাপ ছড়ায়। রুদ্রর অঙ্গ, অঙ্গ সঞ্চালন সবই এত চেনা আমার! কখন সে হাই তুলবে, কখন সে শোয়া থেকে উঠে বসবে, হাতদুটো ঘাড়ের পেছনে নেবে, কখন সে একটি সিগারেট ধরাবে, কোন কাতে শোবে সে, কটা বালিশ প্রয়োজন হয় তার, কথা বলার সময় কোন হাতটি নাড়বে, কোন আঙুলটি, সব জানা আমার। রুদ্রকে তাই চাইলেও ভাবতে পারি না সে আমার আপন কেউ নয়। বিয়ে নামক জিনিসটিকে অদ্ভূতুড়ে একটি ব্যপার বলে মনে হয়। বিয়ে কি সত্যি কাউকে আপন করে, অথবা বিচ্ছেদই কাউকে পর করে! ইচ্ছে হয় বলি, যতদিন ইচ্ছে থাকো এই বাড়িতে, এটিকে নিজের বাড়ি বলেই মনে কোরো।
‘যদি কখনও ইচ্ছে হয় এখানে আসতে, এসো।’ খুব সহজ কণ্ঠে বলি।
রুদ্র ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে।
‘তোমার ওই যে প্রেম চলছিল, সেটি চলছে এখনও?’
রুদ্র শুকনো কণ্ঠে বলে, ‘হ্যাঁ চলছে।’
‘বিয়ে টিয়ে শিগরি করছো নাকি?’
‘করব।’
ম্লান একটি হাসি ঠোঁটের কিনারে এসেই মিলিয়ে যায়। রাতেই আমি রুদ্রর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি দেখি। আঙুলে পচন ধরেছে। কালো হয়ে গেছে আঙুলটি। সকালে হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে চেনা এক সার্জনকে দিয়ে পূঁজ আর পচা রক্ত বের করে রুদ্রর আঙুল ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিয়ে আসি। গ্যাংগ্রিনের আভাস দেখেছি আঙুলটিতে। তবে কি ধীরে ধীরে আঙুলে পচন আরও বেশি ধরবে! পুরো হাতটিই তো পরে কেটে ফেলতে হবে। পেরিফেরাল সার্কুলেশনে তা নাহলে বাধা পড়বে। রক্ত জমাট বেঁধে হৃদপিণ্ডের বা মস্তিস্কের রক্তনালী বন্ধ করে না দিলেই হয়। কি বলব রুদ্রকে! অনেক বেশি শান্ত সে আগের চেয়ে। বড় মায়া হয়। ডান হাতটি সে আর ব্যবহার করতে পারছে না। মুখে তুলে রুদ্রকে ভাত খাইয়ে দিই, মুখ ধুয়ে মুছিয়ে দিই।
রুদ্র যখন যাচ্ছে, তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আঙুলের হাতটি ধরে বলি, ‘যদি কোনও অসুবিধে দেখ, তবে ডাক্তারের কাছে যেও, নয়ত আমার এখানে চলে এসো, আমি তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এরকম পচন ধরা কিন্তু ভাল লক্ষণ নয়।’
ডাক্তার প্রেসক্রিপশান লিখে দিয়েছেন। রুদ্রকে বারবার বলি নিয়মিত ওষুধ খেতে। জিজ্ঞেস করি, ‘টাকা পয়সা কিছু আছে?’
রুদ্র মাথা নাড়ে। মাথা নাড়ে, আছে। হাতে চলার মত টাকা থাকলে মুখে বলত, মাথা নাড়ত না। পাঁচশ টাকা দিতে চাই হাতে। হাতটি সংকোচে টাকাটি ছোঁয় না।
টাকার দিকে তাকিয়ে রুদ্র বলে, ‘তোমার লাগবে তো!’
‘সে আমি বুঝবো। তুমি রাখো এটা।’
চুপ হয়ে থাকে রুদ্র। একটু কি সে লজ্জা পায়! বলি, ‘তুমি তো আমাকে অনেক দিয়েছো, আমি না হয় সামান্য কিছু দিলাম।’
টাকাটি রুদ্রর সার্টের বুকপকেটে পুরে দিই। রুদ্র চলে যায়।
পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা আমার চোখে দু ফোঁটা জল। আবার কখন কোথায় দেখা হবে অথবা আদৌ দেখা হবে কি না আমাদের তা আমরা দুজনের কেউই জানি না।
বাড়িঅলা নোটিশ পাঠান, আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। এই আশঙ্কা আমি আগেই করেছিলাম। যেদিন নাইম এসে দরজা ধাককালো, সেদিনই আশঙ্কার অঙ্কুরটি গেঁথে যায় মনে। ডালপালা ছড়িয়ে বড় হওয়ার আগেই নোটিশ। খোকার দ্বারস্থ হয়েছিলাম নাইমের গন্ধ পেয়েই। খোকা বাড়ি খুঁজতে শুরু করেছেন। যেখানেই যান, আবারও একই সমস্যা, একা একটি মেয়ে থাকবে, বিয়ে শাদি হয়নি? স্বামী নেই? একা মেয়ে কি করে থাকে বাড়িতে? মেয়ে ডাক্তার। ডাক্তার হয়েছে তাতে কি! স্বামী থাকতে হবে। স্বামীহীন মেয়ে ডাক্তার হোক কী ইঞ্জিনিয়ার হোক কী বিজ্ঞানী হোক, কী পতিতা হোক, এক। মেয়ে হল জ্বলজ্যান্ত ঝামেলা। খোকা বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে বাড়িঅলাদের বিদ্রুপ, চোখ কপালে তোলা, আকাশ থেকে পড়া, ভ্রুকুঞ্চন, নাসিকাকুঞ্চন, কপালের ভাঁজ, চু চু চু, অপারগতা ইত্যাদি দেখতে থাকেন, শুনতে থাকেন। ভাড়ার জন্য কোনও বাড়ি পাওয়ার আগেই দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়। সে রাতে মা ছিলেন না বাড়িতে, মা ময়মনসিংহে। সে রাতে মিনার এল। ময়মনসিংহে গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছিল, আমার তো কিছু করতে হয় তার জন্য, তাই নেমন্তন্ন করেছিলাম রাতের খাবারের। হাতে তিনটি বিয়ারের কৌটো নিয়ে এসেছে। বিয়ার শেষ করে সে খাবার খাবে। মিনার বসে বিয়ার খেতে থাকে, আমি যেহেতু বিয়ার পানে অভ্যস্ত নই, এক কাপ চা নিয়ে বসে বসে মিনারের গল্প শুনি। এই মিনারকে দেখলে আমার একটুও মনে হয় না এ সেই আগের মিনার যাকে চিনতাম। যেন এ সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষ। আগের চেয়ে আরও ভদ্র, নম্র, আরও প্রাণবান, আরও গভীর। মিনারের বিয়ার তখনও শেষ হয়নি, তখনই দরজায় শব্দ। দরজায় বাবা আর দাদা দাঁড়িয়ে। দরজা থেকেই বাবা মিনারের দিকে এমন কটমট করে তাকালেন যে আমি মিনারকে বললাম চলে যেতে। না খেয়ে চলে গেল বেচারা। আমার খুব আনন্দ হয় দুজনকে দেখে। এই প্রথম তাঁরা আমার বাড়িতে এলেন। এই প্রথম আমি সুযোগ পাচ্ছি বাবাকে আমার স্বনির্ভর জীবনটি দেখাবার। তাঁরা কি কোনও কাজে এসেছেন ঢাকায়! রাত হয়ে গেছে বলে ময়মনসিংহে ফিরতে পারেননি! নাকি আমাকেই দেখতে এসেছেন! আমি কেমন আছি দেখতে, আমার চাকরি বাকরি কেমন চলছে দেখতে, নিজের বাড়িটি কেমন সাজালাম দেখতে! নাকি এফসিপিএস এর জন্য পড়াশোনা শুরু করেছি কি না দেখতে! নাকি আমার কোনও অর্থনৈতিক অসুবিধে আছে কি না জানতে! জানলে আমাকে সাহায্য করবেন! বাবা কোনও কিছুই বলেন না। উৎসুক বসে থাকি বাবার কথা শোনার জন্য। লিলিকে বলে দিয়েছি শিগরি ভাত চড়াতে। ভাত রাঁধা হলে হলে ভাত দেওয়া হয় টেবিলে। কিন্তু দুজনের কেউই খাবেন না। দুজনেরই মুখ ভার। কেউ কোনও উত্তরও দেন না আমার কোনও প্রশ্নের। বাবা জিজ্ঞেস করেন, ‘যে লোকটি ঘরে ছিল, সে কে?’ প্রশ্নটি বাবা দাদাকে করেন। দাদা আমার দিকে তাকান। আমি বলি, ‘মিনার, বিচিন্তা পত্রিকার সম্পাদক।’ বাবা দাদার দিকে প্রশ্ন চোখে তাকান। দাদা নরম স্বরে বলেন, ‘নাম মিনার, বিচিন্তা পত্রিকার সম্পাদক।’
‘কেন আইছিল এই বাসায়?’ প্রশ্নটি দাদাকে করা হয়। দাদা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘ওই লোক কেন আইছিল?’ আমি বাবার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিই, ‘এমনি।’ দাদা বাবাকে বলেন, ‘এমনি।’
‘ওই লোকের সাথে তার সম্পর্কটা কি?’ বাবা দাদাকে জিজ্ঞেস করেন।
দাদা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘ওই লোকের সাথে তর সম্পর্ক কি?’
আমি কাঁধ নাড়িয়ে বলি, ‘জাস্ট ফ্রেন্ড।’
দাদা বাবাকে বলেন, ‘জাস্ট ফ্রেন্ড।’
টেবিলে ভাত তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাবা বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেন। আর ক্ষণে ক্ষণে দাদাকে ডেকে পিলপিল করে কথা বলেন। কী কথা, আমার সাধ্য নেই বুঝি। কাপড় চোপড় পাল্টাতে হবে তো! দুজন এসেছেন খালি হাতে, কোনও লুঙ্গি গেঞ্জি আনেননি। আমার শাড়ি দেব নাকি লুঙ্গির মত করে পরতে! বাবা দাদার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়েন। না, তিনি কাপড় পাল্টাবেন না। রাতে খাটের বিছানায় যেখানে আমি আর মা ঘুমোই, নতুন চাদর বিছিয়ে দিই দাদা আর বাবার জন্য। ও বিছানায় বাবা বললেন ঘুমোবেন না। কোথায় ঘুমোবেন? তা নিয়ে নাকি আমাকে ভাবতে হবে না। কিছুতেই রাজি হলেন না বিছানায় যেতে! আমি বড় বিছানায় একা রানীর মত শুয়ে থাকব আমি আর নিজের বাবা আর দাদা কার্পেটে শোবেন! দুজনকে ঠেলে যে পাঠাবো বিছানায়, তাও সম্ভব নয়। তাঁরা লোহার মত হয়ে আছেন, শরীরেও, মনেও। খাটে দুটো তোশক নেই যে একটি এনে কার্পেটে বিছিয়ে দেব। বিছানার একটি চাদর দিই পেতে শোবার। কিন্তু বাবা শোবেন না। কি করবেন সারারাত? বসে থাকবেন। দাদাও বসে থাকবেন বাবার সঙ্গে। বাবার হাতে একটি সুগন্ধা। সুগন্ধার মত নিম্নরুচির পত্রিকা বাবা কবে থেকে পড়ছেন, তা জানি না। সুগন্ধা মৌলবাদী গোষ্ঠীর পত্রিকা। একে তাকে গালাগাল, যৌনতা, মিথ্যে সংবাদ, রটনা, ফালতু আলাপ, যা কিছু হলুদ সাংবাদিকতার জন্য প্রয়োজন, সুগন্ধায় সব কিছুর দুর্গন্ধ আছে। শেষ অবদি অনেক রাতে লোহা গলাতে না পেরে আমি শুতে যাই বিছানায়।
সকালে উঠে যখন আমি হাসপাতালে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, দেখি বাবা আর দাদা কাপড় চোপড় পরে তৈরি, তাঁরাও যাবেন। কোথায়? ময়মনসিংহ। আজ থেকে গেলে হয় না? বললেন, হয় না। ঠিক আছে। তারা বললেন কিছুই ঠিক নেই। আমাকে এখন তাঁদের সঙ্গে ময়মনসিংহে যেতে হবে। ময়মনসিংহে কেন? যেতে হবে। যে করেই হোক যেতে হবে। পাগল নাকি! হেসে ফেলি। হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে আমার ডিউটি, আজকে রোগী ভর্তির দিন, এক্ষুনি যেতে হবে। বাবা বললেন, না যেতে হবে না। মানে? মানে আমার আর হাসপাতালে যেতে হবে না। আমার আর চাকরি বাকরি করতে হবে না। আমাকে এক্ষুনি এই মুহূর্তে তাঁদের সঙ্গে ময়মনসিংহে যেতে হবে। আমি বলি, আমি যাবো না। যাবো না বলে যেই না ঘুরে দাঁড়িয়েছি, বাবা চিৎকার করে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েন আমার ওপর। এমন জোরে চড় লাগান গালে যে মনে হয় ঘাড় থেকে যেন ছিটকে পড়ল মাথাটি। ভয়াবহ চড়গুলো আমার মাথায় মুখে মিনা-পর্বতে হাজীদের ছোঁড়া পাথরের মত পড়তে থাকে। বাবা ধাককা দিয়ে আমাকে মেঝেয় ফেলে লাথি কষাতে থাকেন পিঠে পেটে। দৌড়ে গিয়ে বিয়ারের ক্যানগুলো এনে ছুঁড়ে মারেন আমাকে লক্ষ্য করে, কপালে লেগে কপাল কেটে যায়। ঠোঁটে লেগে ঠোঁট কেটে যায়। রক্ত ঝরতে থাকে। দূর থেকে ছুটে এসে আমার চুল ধরে টেনে উঠিয়ে আবার ধাককা দিয়ে ফেলেন আলমারির দরজায়। ধরাম করে মাথাটি গিয়ে পড়ে আয়নায়। আয়নার মুখটিতে চোখ যায়, দেখি কপালের আর ঠোঁটের রক্ত ঝরা। বাবার এমন আগুন হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে আমি তার কিছুই জানি না। আমি হতবুদ্ধির মত চেয়ে থাকি। কাঁপতে কাঁপতে গা শিথিল হয়ে আসে, যেন জ্ঞান হারাচ্ছি। আমার দিকে বাবা ছুঁড়ে দেন সুগন্ধা পত্রিকাটি। পত্রিকাটি আমার গায়ের ওপর পড়ে থাকে। দাদা ওটি তুলে নিয়ে পাতা খুলে মেলে ধরেন আমার সামনে, বলেন, ‘লেখছে তর সব কাহিনী। কি করতাছস সব লেখছে।’ কে আমার কি কাহিনী লিখেছে আদৌ দেখার ইচ্ছে হয় না। মনের শক্তিতে উঠে দাঁড়াই। অ্যাপ্রোনটি হাতে নিয়ে দরজার দিকে যেতে থাকি। বাবা দৌড়ে এসে দরজা ধরে দাঁড়ান।
‘হাসপাতালে যাইতে হইব আমার। দেরি হইয়া যাইতাছে।’ শক্ত গলায় বলি।
তর কোথাও যাইতে হইব না। আমার চেয়ে দ্বিগুণ শক্ত গলায় বলেন বাবা।
আমি চিৎকার করে উঠি, ‘হইব। আমার যাইতে হইব।’ বলতে গিয়ে দেখি গলা কাঁপছে আমার। কান্নায় কাঁপছে।
বাবার রক্তচোখের দিকে তাকানো যায় না, চোখ ঝলসে যায় আমার। আমার যেতে চাওয়াকে তিনি টেনে এনে ছুঁড়ে ফেলে দেন। যেতে চাওয়া কাতর অনুনয় জানায়। বাবা যে আমার হাসপাতালের ডিউটিতে যাওয়ার পথ রোধ করে জীবনে কখনও দাঁড়াতে পারেন, আমার বিশ্বাস হয় না। এই বাবার মুখ দিয়ে কখনও যে উচ্চারিত হতে পারে যে আমার চাকরি করতে হবে না, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। অকল্পনীয় সব ব্যপার চোখের সামনে ঘটতে থাকে। হঠাৎ আমার মনে হয়, এ সত্যি নয়, এরকম ঘটনা সত্যি সত্যি ঘটতে পারে না। এ নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন। নিশ্চয়ই আমি ঘুমিয়ে আছি, আর স্বপ্নের ভেতর দেখছি অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড। ঘুম ভাঙলেই দেখব আমি ধবল বিছানায় শুয়ে, জানলা গলে পূর্ণিমার রং এসে গা ঢেকে দিয়েছে।
আমার কোনও প্রতিবাদ টেকেনি। সুগন্ধা পত্রিকার লেখাটি মিথ্যে এ কথা যতবারই বলি বাবা ধমকে ওঠেন। হাতে নাতে তিনি এক লোককে ধরেছেন আমার ঘরে, রাতে। এর চেয়ে বেশি কী আর প্রমাণ তাঁদের দরকার! অবশ্য এই প্রমাণটি না পেলেও দুজনে ময়মনসিংহ থেকেই পরিকল্পনা করেই এসেছেন কী করবেন। বাবা আর দাদা আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিচে নামান। লিলিকেও নামান দরজায় তালা দিয়ে, চাবি বাবার পকেটে। নিচে অপেক্ষা করে থাকা একটি ভাড়া গাড়িতে আমাকে তোলেন। গাড়ি ময়মনসিংহে পৌঁছে। আমার মন পড়ে থাকে ঢাকায়। মন পড়ে থাকে আমার সুখের সংসারে। পড়ে থাকে হাসপাতালে, আমার অনুপস্থিতি নিয়ে তুলকালাম হচ্ছে নিশ্চয়ই। গাইনি বিভাগের সব ডাক্তারদেরই চোখে পড়ছে আমি নেই। নামটিতে একটি লাল দাগ পড়ছে। নামটিতে একটি ভ্রুকুঞ্চন এসে যোগ হচ্ছে। এই যে ভীষণ উদ্দীপনায় কাজ করছি হাসপাতালে, এতে রোগীর সেবা যেমন হচ্ছে, বিদ্যেটিও আমার আবার হাতে কলমে শেখা হচ্ছে। শেখার, শেখানোর এই উৎসাহই আমাকে নিয়ে যেতে পারত এফসিপিএসের দিকে। এফসিপিএস বড় সংক্রামক, কেউ একজন পড়ছে দেখলে নিজের ভেতর ইচ্ছে জাগে পড়ার। বাবা কি সত্যি সত্যি আমার সমস্ত সম্ভাবনার গলা জবাই করছেন! ভাবতে পারি না।
অবকাশে পৌঁছলে ঘাড় ধরে আমার ঘরটির দিকে আমাকে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন বাবা। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিলেন দরজায়। ওপাশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, ‘এখন এইভাবে এই ঘরে তর সারাজীবন কাটাইতে হইব। তর বাইরে যাওয়া বন্ধ। চাকরি বাকরির খেতা পুরি। ডাক্তারি করতে হইব না। পাখনা গজাইছে তর। তর পাখনা আমি পুড়াইয়া দিতাছি।’
সুগন্ধায় আমাকে নিয়ে লেখাটির শিরোনাম ছিল তসলিমা নাসরিন এখন উড়ে বেড়াচ্ছেন। উড়ে বেড়াচ্ছি আমি আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে। আমাকে রিক্সায় দেখা গেছে আজ লম্বা মত কালো মত এক ছেলের সঙ্গে, কাল ফর্সা মত মোটা মত এক লোকের সঙ্গে ইত্যাদি। আমি মধূ আহরণে ব্যস্ত ইত্যাদি। সুগন্ধার মত পত্রিকার এই কড়া হলুদ লেখাটি আমার সুখের সংসার ধূলিসাৎ করে দিতে পারে, এত শক্তি এর। ছাপার অক্ষরে বাবার প্রচণ্ড বিশ্বাস। যে কোনও কাগজে যা কিছই লেখা থাকে, তিনি তা বিশ্বাস করেন।
সেদিনই ঢাকায় লোক পাঠিয়ে আরমানিটোলার বাড়িতে যা কিছু ছিল সব ট্রাকে তুলে ময়মনসিংহে নিয়ে এসেছেন বাবা। জানালা দিয়ে দেখি উঠোনের কাদা মাটিতে আমার বড় শখের বড় সুখের সংসারের জিনিসপত্র পড়ে আছে। বন্ধ ঘরটির তালার চাবি বাবার বুক পকেটে। আমাকে খাবার দিতে হলে মা বাবার কাছ থেকে চাবি নিয়ে তালা খুলে ভেতরে ভাত রেখে চলে যাবেন, দরজা তালা বন্ধ করে। বাবা এই নিয়ম করে দিয়েছেন। ভেতরে একটি বালতি দেওয়া হয়েছে। ওতে আমার পেচ্ছ!ব পায়খানা বমি কফ থুতু সারতে হবে। পছন্দ না করলেও বাবার নিয়মে চলতে হয় মার। দরজার ওপাশ থেকে মাঝে মাঝে আমার উদ্দেশ্যে সবাই ঘেউ ঘেউ করেন। মাও গলা চড়ান, ‘বালাই ত আছিলি। ব্যাডাইনগর সাথে না মিশলে কী হয়! পত্রিকায় এইসব লেখা উডে কেন? কত মেয়ে আছে, চারদিকে কত মেয়েরা ডাক্তারি করতাছে। সুন্দর ভাবে থাকতাছে। তর জীবনে ত তা আর হইল না। বিয়া যদি না করতে চাস, বালা কথা। কত মেয়ের জামাই মইরা গেছে অথবা বিয়াই করে নাই, তারা একলা থাকে না? তাদের নামে ত এইসব লেখা হয় না। মেয়েদের কথা এত লেখস, ব্যাডাইনগর বদনাম এত লেখস, ব্যাডাইন ছাড়া বাছস না কেন?’
১০. গোল্লাছুট
বন্দী জীবন থেকে মুক্তির কোনও পথ নেই। কোনওদিন মুক্তি পাবো বলে মনে হয় না। নিজ ভূমে পরবাসী হওয়ার যন্ত্রণা অনেক। আমি আমার সকল যন্ত্রণা নিয়ে একা বসে থাকি। হাসপাতাল থেকে বিনা নোটিশে আমার বিচ্ছিত হওয়া দেখে ডাক্তাররা নিশ্চয়ই বিস্মিত এবং বিরক্ত। কিন্তু কী করতে পারি আমি! নিজের জীবনটি নিজের হাত থেকে ফসকে গেল হঠাৎ। আমার অক্ষমতাগুলো আমাকে দুমড়ে মুচড়ে আমাকে ক্ষুদ্র করে ফেলতে থাকে। কষ্ট কান্নায় বুক ভারি হয়ে আছে। কথা বলতে চাই, কাঁদতে চাই কিন্তু পারি না। দিন রাত পড়ে পড়ে গোঙাই কেবল। নিজেকে বকুলির মত মনে হয়। সেই বকুলি। কথা বলতে না পারা বকুলি। বকুলি টিকাটুলির মেয়ে। হাসপাতালে একদিন বকুলির মা তাকে নিয়ে এসেছিল। এর আগে কোনওদিন বকুলি বা তার মা হাসপাতালে আসেনি। হাসপাতালের কোথায় যেতে হয়, কি করতে হয় কোনও চিকিৎসা পেতে হলে, দুজনের কেউই জানে না। সকালে হাসপাতালে ঢুকেই দেখেছি দুজন বসে আছে বহির্বিভাগের বারান্দায়। একজনের ষোল সতেরো বছর বয়স হবে, আরেকজনের বয়স অনুমান করি তিরিশের মত। হাসপাতালের আঙিনায় এরকম কত মানুষই তো বসে থাকে। কিন্তু বারান্দায় চোখ পড়তেই দেখি অল্প বয়সী মেয়েটি আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। কেন তাকিয়ে আছে, আমাকে কি চেনে নাকি! একবার মনে হয়, হয়ত আমার রোগী ছিল কোনও এক সময়, তাই চিনেছে। আমি গাইনির বর্হিবিভাগে রোগী দেখতে ঢুকে যাই। দুপুরবেলা বেরিয়ে দেখি ওরা দুজন ঠিক একই জায়গায় একই রকম করে বসে আছে। আমি কি জানি কেন ধীরে ধীরে বসে থাকা দুজনের দিকে এগিয়ে যাই, বলি, ‘রোগী কে?’
‘বকুলি।’
‘ওর নাম বুঝি বকুলি!’
‘হ আমার মেয়ে। আমার মেয়ে বকুলি।’ তিরিশ হাত রাখেন ষোলর পিঠে।
‘কি অসুখ?’
‘বকুলি কথা কয় না।’
‘অসুখ কি? কি জন্য আসছেন এইখানে।’
‘বকুলি কথা কয় না।’
‘কথা কয় না তো বুঝলাম, অসুখ টা কি? পেটে অসুখ. নাকি বুকে অসুখ। বলেন, কিসের চিকিৎসা করতে চান।’
‘বকুলির কথা ফিরাইয়া দেন। বকুলি যেন আবার আগের মত কথা কয়।’
‘কবে থেইকা কথা কয় না?’
‘আজকে একমাস হইয়া গেল কোনও কথা কয় না।’
বকুলি আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, বড় ডাগর চোখে। কী আশ্চর্য সুন্দর চোখ। এরকম চোখ যদি আমার থাকত, মনে মনে ভাবি। বিধ্বস্ত চুল। কপালে ঘামে ভেজা কিছু চুল লেপটে আছে। পরনে একটি নীল সুতি শাড়ি। আলু থালু।
‘কেন কথা কয় না?’
‘তা তো জানি না।’ মহিলা মাথা নাড়ে। বকুলির দিকে তাকিয়ে এরপর বলে, ‘বকুলি কথা ক। ক কি হইছিল। কথা ক বকুলি। ও বকুলি কথা ক। একবার কথা ক। ক কথা। কথা ক।’
‘কী হইছিল যে কথা কয় না! একমাস আগে কিছু কি ঘটছিল?’
বকুলির মা এদিক ওদিক তাকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আসে আমার দিকে, আমার খুব কাছে এসে কানের কাছে মুখ রেখে আস্তে বলে, ‘ও নদীর ধারে পইড়া ছিল। মানুষে আইয়া খবর দিলে আমি গিয়া নিয়া আইছি।’
‘পইড়া ছিল কেন?’
‘কী জানি, কারা নাকি ধইরা নিছিল। গেছিল ত কামে। জিনজিরার ফ্যাক্টরিতে কাম করত। কাম থেইকা দুইদিন ফিরে নাই। পরে ত খবর পাইলাম।’
‘যখন নদীর পাড়ে পইড়া ছিল , জ্ঞান ছিল?’
‘তা ছিল। আমার সাথে উইঠা আইল। আমি তারে নিয়া আইলাম বাড়িত। এত জিগাইলাম কী হইছিল ক। বকুলি কথা কইল না। সেই যে কইল না। আইজও কয় না।’
‘খারাপ কিছু ঘটছিল নাকি?’
‘মানুষে কয় ব্যাটারা নাকি তার ইজ্জত নিছে।’
বকুলির মা ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে। কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে, ‘এক আশ্বিন মাসে বকুলি হইল, পরের আশ্বিনে তার বাপ মরল।.. ‘ আমার সময় নেই বকুলির মার গল্প শোনার, থামিয়ে দিয়ে বলি, ‘কালকে সকালে আইসা নাক কান গলা বিভাগে যাইয়া ডাক্তার দেখান। গলায় হয়ত কোনও অসুবিধা থাকতে পারে।’
আমি সরে আসি। প্রতিদিনই আমাকে মানুষের কষ্টের গল্প শুনতে হয়। হাজারও রকম কষ্টের মধ্যে এও এক কষ্ট।
বকুলির মা আমাকে পেছন থেকে ডাকে, ‘আপা, বকুলি কি কথা কইব না আর?’
‘জানি না।’
আবারও ডাকে, ‘আপা একটু খাড়ন।’
দাঁড়াই।
‘আপনের বড় মায়া। বকুলি যেন কথা কয়, এই ব্যবস্থাটা কইরা দেন। বোবা মেয়ে নিয়া আমি এখন কই যামু, কি করমু।’
‘কালকে আইসা ডাক্তার দেখান। শুনেন ডাক্তার কি কয়।’ হাঁটতে হাঁটতে বলি।
হাসপাতালের গেটের কাছ থেকে একটি রিক্সা নিয়ে উঠে বসি। তখনও বকুলি ওভাবেই বসা ছিল। বারান্দা থেকে বকুলির মা আমার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। সারা পথ আমার কানে কেবল বকুলির মার কথাটি বাজল,বকুলি কথা ক।
পরদিন বর্হিবিভাগের বারান্দায় আমার চোখ যায়, বকুলি যেখানে বসে ছিল। অনেক রোগীর ভিড়, কিন্তু বকুলি নেই, বকুলির মাও নেই। পরদিনও দেখি। না, বকুলি নেই। হয়ত এসেছিল, ডাক্তার দেখিয়েছে, ডাক্তার বলে দিয়েছে, বকুলির গলায় কোনও রোগ নেই। বকুলির মা নিশ্চয়ই তখন বারবারই বকুলিকে বলছিল, ‘বকুলি কথা ক, কথা ক বকুলি।’ সেই থেকে বকুলিকে খুঁজি আমি মনে মনে। হাসপাতালে ঢুকলেই বসে থাকা রোগীদের মধ্যে বকুলির মুখটি খুঁজি। খুব জানতে ইচ্ছে করে বকুলি কি শেষ পর্যন্ত কথা বলেছে কি না।
আমার নির্বাচিত কলাম ওদিকে শীতের সকালের মুড়ির মত বিক্রি হচ্ছে। খোকা একটির পর একটি সংস্করণ ছেপে যাচ্ছেন। এদিকে বন্দী আমি। জেলখানার দাগী আসামীর মত বন্দী। দাগী আসামীকে সম্ভবত এত গালিগালাজ করা হয় না, যত করা হয় আমাকে। বাড়িতে অতিথি এলেও উঁকি দিয়ে একবার দেখে যায় আমার বন্দীদশা। বাড়ির কুকুর বেড়ালও দেখে দরজার ফাঁক দিয়ে। হাঁস মুরগি হাঁটছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে উঠোনে, আহা ওদের মত স্বাধীনতাও যদি আমি পেতাম! পরাধীনতা কাকে বলে আমি হাড়ে মজ্জায় টের পাই। চিৎকার করি, সকলে শোনে, কিন্তু তালা খোলে না। যে কাপড়ে এসেছিলাম, সেই কাপড়টিই পরা, আর কোনও কাপড় নেই যে পাল্টাবো। গোসলহীন গা থেকে বিশ্রি গন্ধ বেরোতে থাকে। ঘরে একটি বই নেই যে পড়ব। কোনও টেলিভিশন নেই যে দেখব, কোনও গানের যন্ত্র নেই যে গান শুনব। কোনও মানুষ নেই যে কথা বলব। কেবল শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমার আর করার কিছু নেই। আমার এখন চোখে কোনও জল নেই যে জমবে। দুটো গালে জল শুকোতে শুকোতে দাগ পড়ে গেছে। দুশ্চিন্তা এসে পাশে শুয়ে থাকে, দুর্ভাবনার কণিকারা এখন রক্তের লাল সাদা কণিকার মত আমার রক্তে ভাসছে। সামনে একটি ঘোর কালো অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির কারণে চাকরিটি একদিন আমার চলে যাবে। কী করে আবার নিজের ভাঙা বাড়িঘর গুছোবো আমি! স্বপ্নের দালানকোঠা ধ্বসে পড়েছে। স্বপ্নহীন, ভবিষ্যতহীন, মরা মানুষের মত শুয়ে থাকি। এই আমাকে আমি চিনি না। এই আমার নাম আমি জানি না। যখন দলিত মথিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত আমি সাহসে বুক বেঁধে উঠে দাঁড়িয়েছি, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, সুন্দর একটি জীবন গড়ে তুলছি, তখনই আবার আমাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলা হল। বাবা জানেন না, বাবা আমার জীবনের কতটুকু ক্ষতি করেছেন। তাঁর মত লোকের কোনওদিনই জানা হবে না। কোনওদিনই তিনি কাছে এসে বসবেন না, জিজ্ঞেস করবেন না কোথাও কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না, হলে কী অসুবিধে, কোনওদিন জানতে চাইবেন না আমার সুখ বা দুঃখ বলে কিছু আছে কি না। এভাবে কত দিন আমাকে বন্দী করে রাখা হবে! কত মাস! কত বছর! কী অপরাধের শাস্তি আমি পাচ্ছি! আদৌ কি কোনও অপরাধ আমি করেছি! আমার লেখার প্রশংসা যেমন হচ্ছে, ইচ্ছেমত নিন্দাও হচ্ছে। এসবে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি। সস্তা পত্রিকাগুলোয় প্রায়ই আমাকে নিয়ে লেখা হয়, আমাকে কুচি কুচি করে কাটা হয় সেসব লেখায়। আমার লেখা নিয়ে আলোচনা না করে কেবল মেয়ে হয়েছি বলে ব্যক্তিগত জীবন ঘাঁটে কিছু লোক। কেবল মেয়ে হয়েছি বলে খুব সহজে চরিত্রে কালিলেপন হয়ে যায়। বলে দিলেই হল যা ইচ্ছে তাই। মেয়েদের নিয়ে রটনা ঘটনা জিভে খুবই রোচে। কিছু লোক আমাকে নিয়ে মজা করছে বলে আমাকে বন্দী জীবন যাপন করতে হবে! এতে কি আমার না কি আমার বাবার মার আমার ভাই বোনের এক রত্তি কিছু লাভ হচ্ছে! বাবা জানেন না সুগন্ধায় আমার সম্পর্কে এসব লেখার মূল উদ্দেশ্যটি। বাবা জানেন না যে পত্রিকার লোকেরা পত্রিকার বিক্রি বাড়াবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে মজাদার মুখরোচক খবর ছাপে। আমার জীবন জানার জন্য বাবার উচিত ছিল আমাকে জিজ্ঞেস করা, আমার জীবনের খবর আমার চেয়ে বেশি সুগন্ধার কোনও লোক জানে না। বাবার ওপর আমার রাগ হয়। ভীষণ রাগ হয়। ভীষণ রাগে আমি ছটফট করি। এ ঘরটি একসময় আমারই ঘর ছিল, এখন এই ঘরটিকে একটি কফিন বলে মনে হয়। যে আমি অসম্ভব সাহস আর দৃঢ়তা অনুভব করতাম নিজের ভেতর, সেই আমি দেখি হাত পা ছোঁড়া শিশুর মত। পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল বলে পাখিকে খাঁচায় এনে বন্দী করেছেন বাবা। আমাকে জন্ম দিয়েছেন, সেই অধিকারে তিনি ভেবেছেন তাঁর যা খুশি তিনি তা করতে পারেন। আর কতকাল আমাকে সইতে হবে তাঁর প্রভুত্ব, রাজত্ব, তাঁর নির্মমতা, তাঁর নির্বুদ্ধিতা! জন্মের ঋণ কি মৃত্যুর আগে শেষ হয় না! নিজের জীবনকে কি নিজের পছন্দ মত যাপন করার অধিকার আমার নেই! আমি ভেঙে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকি। এত অসহায় আমি বোধহয় কখনও বোধ করিনি জীবনে। আমার লেখা পড়ে অনেকে বলে আমি নাকি সাহসী, আমি নাকি মেয়েদের শক্তি যোগাচ্ছি! তারা যদি দেখতে পেত কিরকম শক্তিহীন আমি, কি রকম সহায়সম্বলহীন, কি রকম অন্যের হাতে বাঁধা!
যে অবকাশ আমার চেতনায়, আমার স্মৃতিমেদুরতায়, যে অবকাশ আমার ভালবাসার ধন, সেই অবকাশকে হাবিয়া দোযখের মত মনে হয়। অবকাশ থেকে শেষ অবদি আমি পালাই। সকালে দরজার তালা খুলে মা মাত্র নাস্তা দিয়ে গেছেন, রান্নাঘর থেকে সুফির চিৎকার আর থালবাসন ভাঙার শব্দ শুনে তালা না লাগিয়েই মা দৌড়ে যান রান্নাঘরে। এ সময় পাহারা বসা নেই বৈঠক ঘরে। বাবা নেই বাড়িতে। দাদা ফার্মেসিতে। আমি যে কাপড়ে যেমন ভাবে ছিলাম, তেমনি দৌড়ে বেরিয়ে যাই। দ্রুত হাঁটতে থাকি আঁকাবাঁকা গলিতে। যে গলিতে আমি যেতে পারি বলে কেউ ধারণা করবে না। দৌড়োনোও সম্ভব নয়। দৌড়োলে লোকের সন্দেহ হবে। পেছনে আমি দেখতে চাই না কেউ আমাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিতে আসছে কী না। যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি চাইছিলাম তখন, সেটি একটি রিক্সা, যেমন তেমন রিক্সা। সেটিকে বাড়ির পেছনের দিকে সুতিয়াখালি হাউজের দিকে যে রাস্তায় অবকাশের কেউই যায় না, সেদিকে যেতে বলি। আমি পালিয়েছি খবর পেয়ে কেউ আমাকে দৌড়ে ধরতে গেলে সেরপুকুর পাড়ের দিকে বা গোলপুকুরপাড়ের দিকে যাবে। সুতিয়াখালির গলি পার হয়ে রিক্সাকে যখন রাজবাড়ি ইশকুলের সামনে নিয়ে যাচ্ছি, বলি টাঙ্গাইল যাওয়ার বাসস্ট্যাণ্ডে যেতে। ঢাকা যাওয়ার বাসস্ট্যাণ্ডে পালানোর খবর পেয়ে বাবা স্বয়ং গিয়ে হাজির হতে পারেন।। টাঙ্গাইল যাওয়ার বাসস্ট্যাণ্ডে লোকাল ছাড়া আর বাস ছিল না। বাসে উঠেও আমার হৃদকম্প থামে না। লোকাল বাসেই উঠে পড়ি, লোকাল বাস টাঙ্গাইল যাওয়ার পথে যত বাসস্ট্যাণ্ড আছে সবকটাতে থেমে থেমে যাবে। আমার পক্ষে বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে এক্সপ্রেস বাসের জন্য অপেক্ষা করাও নিরাপদ নয়। কোনও থামাথামি না করে এক্সপ্রেস বাস সোজা টাঙ্গাইল যায়। কতক্ষণে এক্সপ্রেস এসে থামবে এখানে তার কোনও ঠিক নেই। বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করতে গেলে কেউ আমাকে চিনে ফেলতে পারে, কেউ খবর দিতে পারে বাবাকে অথবা বাবাই ঢাকার বাসস্ট্যান্ডে আমাকে না পেয়ে টাঙ্গাইল বাসস্ট্যাণ্ডে আমাকে খুঁজতে আসতে পারেন। রেলইস্টিশিনেও যেতে পারেন, তাই সেদিকে পা দিইনি। লোকাল বাসটি লককর ঝককর মুড়ির টিন। শহর এলাকাটি বাস যেন দ্রুত পার হয়, যেন খুব দ্রুত পার হয়। বার বার জানালার দিকে আমার অস্থির চোখদুটো চলে যাচ্ছে। বুকের দপদপ শব্দ আমি চাইলেও থামাতে পারছি না। বাসটি ধীরে ধীরে লোক তুলতে তুলতে লোক নামাতে নামাতে বাসের গায়ে থাপ্পড় মারতে মারতে এগোতে থাকে। আমি মেয়ে বলে সাধারণ কোনও সিটে আমাকে বসতে দেওয়া হয়নি। ড্রাইভারের পাশে যেখানে ইঞ্জিনের গরম এসে গা পুড়ে যেতে থাকে, যেখানে পা রাখার কোনও জায়গা নেই, দুটো পা কে বুকের কাছে মুড়ে বসে থাকতে হয় এবং কোনও নড়ন চড়ন সম্ভব নয়, সেই অসাধারণ সিটে বসতে হয়েছে। বাস পুরো আটটি ঘণ্টা নেয় টাঙ্গাইল পৌঁছতে। টাঙ্গাইলে নেমে ঢাকার বাস কোত্থেকে ছাড়ে খবর নিয়ে নিয়ে সেদিকে যাই। ঢাকার বাসে চেপে যখন ঢাকা এসে পৌঁছি, রাত তখন এগারোটা। কোথায় যাব আমি এত রাতে! আমার তো একটি ঘর ছিল, আশ্রয় ছিল। সেটি নেই। আত্মীয়স্বজন কাউকেই আমার আর আপন বলে মনে হয় না। আমি এদের সবার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাই। আমি যাদের কাছে এত ব্রাত্য, তাদের আমি এই মুখ দেখাতে চাই না। তাদের সামনে আমার অনাকাঙ্খিত উপস্থিতি ঘটিয়ে চাইনা বিব্রত করতে। একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকলে অন্তত ফোন ব্যবহার করার সুযোগ পাবো। ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। তার চেয়ে মন চোঁ চোঁ করছে বেশি। কার কাছে কার বাড়িতে আমি আশ্রয় চাইতে পারি এখন! মাথা ঘুরোচ্ছে, বেশিক্ষণ মাথাটি আমাকে ভাবতে দেয় না। মুখস্ত ছিল মিনারের ফোন নম্বরটি। সেটিতেই ডায়াল ঘোরাই। মিনার খবর শুনে অবাক! সে নাকি একদিন ফোন করেছিল হাসপাতালে, হাসপাতাল থেকে বলে দিয়েছে আমি ছুটিতে আছি। কেমন ছুটি কাটিয়েছি আমি তা আর তাকে বলি না। শুধু জিজ্ঞেস করি, এই রাতটা কি তার বাড়িতে আমি থাকতে পারব! মিনার একবাক্যে রাজি হয়। মোটর সাইকেলে এসে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। আমাকে, বৈঠক ঘরে একটি বাড়তি বিছানা ছিল অতিথিদের শোবার জন্য, দেওয়া হয়। পরদিন পার হয়। কী করে পার হয় আমি তার কিμছু জানি না। ঘুমিয়ে! অনেক ঘুম বাকি ছিল আমার। মনের ওপর যে ঝড় গেছে, সেটি শান্ত করতে আমার দরকার ছিল সাতদিন টানা বিশ্রামের। কিন্তু তার পর দিন মিনার বলল, তার মা নাকি বলছে এভাবে একটি মেয়ের এখানে থাকা ঠিক নয়, লোকে মন্দ বলবে, মিনার যেন আমাকে বিয়ে করে নেয়, তাহলে আমার থাকাটা এখানে জায়েজ হবে। সেদিনই শুনেছি এক লোক নাকি এসেছে সবুজ একটি খাতা নিয়ে, খাতাটি মিনার আমার কাছে নিয়ে আসে, নিয়ে আসে সই নিতে। আবার সেই সই। আমি বোধবুদ্ধি লোপ পাওয়া মানুষের মত সই করি। সইএর গূঢ় অর্থ কী তা বোঝার বা ভাবার সময়টুকু নিইনি। সই কেন করি, বাবার ওপর রাগ করে! আর কোনও আশ্রয় নেই বলে! এ দুটোর কোনওটিই আমি এখন মানতে পারি না। বাবার ওপর রাগ আমার অনেক হয়েছে, রাগ করে সই করা কেন, রাগ করে দেখিয়ে দেওয়া যেত যে যে জীবন আমি যাপন করছিলাম, সেই স্বনির্ভর জীবন আমি যাপন করার শক্তি সাহস স্পর্ধা সবই রাখি। কোনও আশ্রয় নেই তা ঠিক, কিন্তু আশ্রয় কেন আমি খোঁজার চেষ্টা করিনি! হাসপাতালে ডাক্তারদের জন্য কোনও হোস্টেল নেই, না থাক, মুখ নত করে হলেও কেন যাইনি আত্মীয়দের বাড়িতে! কেন ছোটদার বাড়িতে গীতার অত্যাচার সয়েও থাকিনি! কেন বড়মামার বাড়িতে বলে কয়ে জায়গার অভাব হলেও মেঝেতে ঘুমোবার ব্যবস্থা করিনি! রাতে ঘুমোনোর জন্যই তো! অপেক্ষা করতে পারতাম তার চেয়ে, খোকা হয়ত আমার জন্য কোনও বাড়ি পেতেন ভাড়া নেওয়ার! কেন আমি খোকাকে ফোন না করে মিনারের কাছে ফোন করেছি, অত রাতে খোকার দোকান খোলা থাকে না, খোকার বাড়ির নম্বর জানা ছিল না, কিন্তু পরদিন সকালেই কেন খোকাকে ফোন করে তার সহযোগিতা ভিক্ষে চাইনি! নাকি আমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলাম! নাকি সত্যি সত্যিই ধিককার দিতে শুরু করেছিলাম স্বামীহীন জীবনকে! নাকি আর দশটা মেয়ের মত স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করার সাধ হয়েছিল হঠাৎ! নাকি মিনারকে আমি ভালবেসেছিলাম! নাহ! ভালবাসা ওই দুদিনের দেখায় আর কথায় হয় না। নাকি পুরুষের নিবিড় আলিঙ্গন চাইছিলাম! স্পর্শ চাইছিলাম! উত্তাপ চাইছিলাম! তাই ছোট্ট একটি সইএর মধ্য দিয়ে সেই স্পর্শ, সেই উত্তাপ নিয়ে শরীরের গভীর গহন খেলাটি চাইছিলাম! দীর্ঘদিনের অতৃপ্ত শরীর চাইছিল তৃপ্ত হতে। একটি পুরুষ-শরীরের জন্য ভেতরে বান ডাকছিল! নাকি নিজেকে এতিম, অনাথ, নিস্পেষিত, গলিত দলিত কীটের মত মনে হচ্ছিল। এ জীবন কার পাতে গেল কার হাতে গেল তা নিয়ে ভাবনা করার কোনও কারণ দেখিনি! আমি ঠিক জানি না কী সেটি!
এক বাড়িতে থাকার জন্য বা এক বিছানায় রাত কাটানোর জন্য সইটি খুব প্রয়োজন। সই ছাড়া যদি কোনও ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়, তবে ছেলের দোষ হয় না, দোষ হয় মেয়ের। মেয়েকে ছিনাল, বেশ্যা, মাগী, বদ, রাক্ষুসে ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। মিলনের সঙ্গে মিলন হওয়ার পর আমি জানি সই ছাড়াও মিলন হওয়া সম্ভব। আসলে কোনও সইই আমাকে বিয়ের কোনও অনুভূতি দেয় না। মিনারের নতুন আবরণটি দুদিনেই খসে গিয়ে আগের সেই মিনার, মোহাম্মদ আলী মিনার, কবিতার স্বামী বেরিয়ে আসে। কবিতার স্বামী কবিতার জন্য আকুল হয়ে কাঁদে, কবিতার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এই শোকে সে কাঁদে। জীবনে কি বিচ্ছিরিরকম ওলোট পালোট এসে গেছে। ইচ্ছে হয় সময়কে পেছনে নিয়ে যেতে, ইচ্ছে করে দেখতে মিনার আর কবিতা দুজন আবার আগের মত দুজনকে ভালবাসছে, দুজনে সুখে সংসার করছে।
হাসপাতালে কেউ খুব বেশি অবাক হয় না আমার ওই কদিনের অনুপস্থিতি নিয়ে। যে দিন বাবা আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যান আরমোনিটোলা থেকে, সেদিন সকালেই আমি জানি না যে বাবা আমার ছুটির একটি দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গাইনি বিভাগে। হাসপাতাল থেকে খোকার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। খোকা আমাকে জানান যে তিনি শান্তিবাগে একটি বাড়ি পেয়েছেন ভাড়ার জন্য। বাড়িঅলাকে বলেছেন তাঁর বোন ভাড়া নেবে বাড়ি, বোন ডাক্তার, একা থাকেন। বাড়িঅলা শিক্ষিত ভদ্রলোক। তিনি রাজি। বাড়িটি দোতলা, সুন্দর বাড়ি। ঝকঝকে। মিনার এদিকে বাড়ি খুঁজছে। সে একটি বড় বাড়ি খুঁজছে, অনেকগুলো শোবারঘরঅলা বাড়ি। তার আত্মীয়স্বজন থাকবে তার বাড়িতে। আমার ইচ্ছে শান্তিবাগের বাড়িটি ভাড়া নেওয়ার। সেটিই নিই। মিনারকে নিয়ে শান্তিবাগের বাড়িতে উঠি। আমাদের অনেকটা যার যার তার তার জীবন শুরু হয়। হাসপাতালে চলে যাই খুব সকালবেলা। সারাদিন মিনারের সঙ্গে আমার দেখা হয় না। আমি হাসপাতালে যাওয়ার পর সে বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাত করে। হয় মাতাল, নয় হাতে প্রতিরাতেই একটি মদের বোতল। ঘরে বসে পুরো বোতল না হলেও অর্ধেক বোতল সে শেষ করে খেয়ে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে বিচিন্তার জন্য সম্পাদকীয় লেখে। মিনার যা কিছুই লেখে খুব দ্রুত লেখে। কাটাকুটি নেই, কলম থামিয়ে রেখে কখনও ভাবতে হয় না কি লিখবে। মদ তার মাথা খুলে দেয়। তবে যা কিছুই লেখে সে, ভাল লেখে। মিনার ইচ্ছে করলে খুব ভাল গল্প লেখক হতে পারত। আমি জানি না কেন সে ও কাজে হাত দিয়েও আবার বাদ দিয়েছে। হঠাৎ একদিন মদ খেতে খেতেই সে বলে পূর্বাভাস পত্রিকায় যেন আমি লেখা বন্ধ করে দিই। আমি কোনও কারণ খুঁজে পাই না আমার লেখা বন্ধ করার। এই পত্রিকায় আমার এই লেখা কোনও লেখাই হয়নি, ওই পত্রিকায় আমার ওই লেখা না লিখলেও চলত, ইত্যাদি অভিযোগ শুনে আমার মনে হতে থাকে, মিনার আমাকে দলামোচা করে খুব ক্ষুদ্র বানিয়ে তার হাতের মুঠোয় নিতে চাইছে। অমাতাল মিনারকে হয়ত বাইরের লোকেরা দেখে, আমার খুব একটা সুযোগ হয় না। আমি যতক্ষণ মিনারকে দেখি, মাতাল মিনারকেই দেখি। প্রতিরাতে তার মদ খাওয়া চাই। বাধা দিয়ে কাজ হয় না। সে খাবেই। শেষরাতের দিকে ঘুমোতে আসে। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে এক সঙ্গম ছাড়া আর কিছুই থাকে না। সঙ্গম তুচ্ছ কোনও ব্যপার নয়। শরীর চায় এই সঙ্গম। শরীর জেগে ওঠে প্রতিরাতে। যে ব্যপারটি আমার জানা ছিল না, কিন্তু খুব শিগরি জানা হয় তা হল, মিনারের সঙ্গে দীর্ঘ বছর ধরে এক ধনী মহিলার প্রেম। মহিলা বিবাহিত। ইস্কাটনে মিনার যে বাড়িতে থাকত, সেটি ওই মহিলারই বাড়ি ছিল। মহিলার সঙ্গে প্রেমে কদিন ভাটা পড়লে মিনার আমার দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু অচিরে প্রেম আবার জেগে ওঠে। আবার তাদের আগের মত দেখা হতে থাকে। কোনও একটি দিন নেই যে মদ না খেয়ে মিনার কাটাতে পারে। সে এরকমই ছিল। মদ খেয়ে রাতে এখানে ওখানে ফোন করত, আমাকেও করত হাসপাতালে। আমি ফোনে কোনও মদের গন্ধ পেতাম না, ভাবতাম ফোনের ওপারের মানুষটি বুঝি খুবই রসঘন প্রাণঘন ঘনশ্যাম। হায়! মাতাল কোনওদিন গলা ফাটিয়ে হাসছে, কোনওদিন বেধড়ক চিৎকার করছে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করছে, কোনওদিন প্যাণ্টের বেল্ট খুলে চাবকাচ্ছে। কোনও কারণ ছাড়াই করছে। ইচ্ছে হচ্ছে বলে করছে। বাড়িটির দোতলাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, দুভাগের একভাগে থাকে সোমারা। সোমা একুশ বাইশ বছর বয়সী একটি মেয়ে, প্রায়ই আমার সঙ্গে গল্প করতে আসে, মাতালের কাণ্ড কারখানা সীমা ছাড়িয়ে গেলে রাত বিরেতে এই সোমার কাছে আমাকে বাকি রাতটুকু পার করার জন্য আশ্রয় চাইতে হয়। উন্নাসিক মাতালটি কোন রাতে কি করবে তা কেউ জানে না। চুমু খাবে না চাবকাবে। মাতাল এক রাতে বাড়ি ফিরে ঘুমের মেয়েটিকে তুলে চাবকাতে থাকে। কি কারণ জানতে চাইলে কোনও উত্তর নেই। গালে শক্ত শক্ত চড় দিয়ে গাল লাল করে ফেলে। চোখে ঘুসি মেরে চোখের রক্ত ঝরায়। গলা টিপে ধরে, আমি পারি না তার শক্ত আঙুলগুলো থেকে নিজেকে বাঁচাতে। নিজেই একসময় ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে দরজার বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে দেয়। সিঁড়িতে বসে রাত পার করতে হয়। পরের রাতেও এই হয়। সিঁড়ি থেকে আবার টেনে হিঁচড়ে ভেতরে নিতে চাইলে পরের রাতে রক্তাক্ত আমি প্রাণে বাঁচার জন্য দৌড়ে গিয়ে বাড়িঅলার বাড়িতে আশ্রয় নিই। লজ্জায় মাথা নত হয়ে থাকে। লজ্জা ভয় ঘৃণা হীনমন্যতা আশঙ্কা আমাকে কুঁকড়ে রাখে। আমি তো একাই ছিলাম, আমি সেই একাই আছি। আগে উপদ্রব ছিল না, এখন জলজ্যান্ত উপদ্রুব চোখের সামনে। ছি ছি ছি! এ কী করেছি আমি! কাকে আমি আমার আশ্রয় ভেবেছি! নিজে কি নিজের জন্য যথেষ্ট ছিলাম না! কিসের অভাব ছিল আমার! ঘৃণায় আমি মিশে যেতে থাকি মাটিতে, নিজের ওপর ঘৃণা আমার। নিজেকে এতটা অসন্মানিত হতে, এতটা হীন দীন হতে আমি নিজেই দিয়েছি। কী প্রয়োজন ছিল আমার অন্যের আশ্রয়ের! স্বামী নামক নিরাপত্তার! কী প্রয়োজন ছিল সমাজের সাধ মেটানোর! স্বামী সন্তান সংসার ইত্যাদির সামাজিক কাদায় কী ভীষণ ডুবে গেছি, যত বেরোতে চাই তত যেন পাকে পড়ি, টেনে নিয়ে যায় আরও গভীরে। রীতির জালে অন্যের মুখ চেয়ে নিজেকে জড়িয়েছি। নিজেই নিজের গলায় দড়ি দিয়েছি। লোকে এই দড়ি দেখলে পছন্দ করে বলে! আমি আর দড়িছেঁড়া গরু নই বলে! কলুর বলদের মত ঘুরছি! খামোকা বিয়ে নামের একটি কলংকের বোঝা ঘাড়ে চাপল। আমার বোধোদয় হবার পরও বোধ হারিয়েছিলাম, আবার নতুন করে বোধের উদয় হল। বিয়ে করলেও কলংক, না করলেও কলংক। যে কোনও একটি কলংক যদি আমাকে বরণ করতেই হয়, তবে বিয়ের কলংককে কেন! এই শিক্ষাটি কি আগে আমার হয়নি! তবে কেন আবার দুর্ভোগ পোহাতে যাওয়া! পুরুষমানুষকে চেনা কি আমার হয়নি! তবে কেন আবার চিনতে যাওয়া! কেন আবার স্বপ্ন রচনা করা! কেন ভাবা যে একজন যে কষ্ট আমাকে দিয়েছে, আরেকজন হয়ত সেই কষ্ট দেবে না! বোকা বুদ্ধু মেয়ে, কষ্ট ওরা দেবেই। এক রকম না হলে আরেক রকম! তুমি কারও ওপর আর নির্ভর কোরো না। কেউ সুখ দেবে তোমাকে, এই আশাটি আর কোরো না। আমি একাধিক বিয়ে করেছি, তার মানে একাধিক পুরুষের সঙ্গে শুয়েছি আমি, এই কলঙ্কটি আমার ত্বকের মত আমার গায়ে সেঁটে থাকে। লোকে আমার ত্বক দেখলেই কলঙ্কিনী বলে আমাকে বিচার করে। এমনকী রুদ্রও। এর মধ্যে দু বার রুদ্রর সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রথম দেখাটি ইত্যাদিতে, ইত্যাদি থেকে বেরিয়ে সেই ভীষণ ঝড় বৃষ্টির রাতে কোনও রিক্সা খালি পাওয়া যাচ্ছিল না, কোনও বেবি ট্যাক্সিও না। অপেক্ষা করতে করতে একটি বেবি পাওয়া গেল, তখন আরেকটির জন্য অপেক্ষা না করে রুদ্র আমার নেওয়া বেবিতে উঠে পড়ল। আমাকে শান্তিবাগ নামিয়ে দিয়ে সে ইন্দিরা রোডে চলে যাবে। সেদিন সেই ঝড়ের রাতে আধমাতাল রুদ্র আমার কোমর জড়িয়ে ধরে কোমরে চাপ দিয়ে বলল, তোমাকে খুব পেতে ইচ্ছে করছে! কী রকম পেতে! রুদ্র চোখ নাচায়। আমার শরীরটি পেতে তার ইচ্ছে করছে। কোমর থেকে তার হাতটি সরিয়ে দিয়ে মালিবাগের কাছে মাথা ভরা বৃষ্টির রাস্তায় নেমে যাই। গালে মুখে জলের বিন্দু, কোনটি বৃষ্টির, কোনটি চোখের জলের, জানি না। দীর্ঘ একটি শ্বাস যন্ত্রযানের শব্দের তলে চাপা পড়ে যায়। রুদ্রকে বিদায় দিয়ে মনে মনে বলি, ইচ্ছে হলে আমি তোমার সঙ্গে শুতে পারি। আরমানিটোলায় আমি ইচ্ছে করেছিলাম। এখন আমি ইচ্ছে করছি না। এতকাল অন্যের ইচ্ছের মূল্য দিয়েছি, এবার নিজের ইচ্ছের মূল্য দিতে চেষ্টা করছি। রুদ্রর সঙ্গে এর পরের দেখাটি সাকুরায়। কথা ছিল সাকুরায় দেখা হবে। রুদ্র আমাকে বলেছে সে তার সমগ্র বের করতে চায়। যত লেখা এ যাবৎ লিখেছে, সব মিলিয়ে একটি বই। আমি যেন তাকে সাহায্য করি। কী রকম সাহায্য! আমি যেন আমার প্রকাশককে দিয়ে তার সমগ্র ছাপার ব্যবস্থা করি। আমার বই ভাল চলছে, সে কারণে প্রকাশক যে আমার সব দাবি মেনে নেবেন, তা নয়। আমি খোকাকে কদিন বলেছি, রুদ্রর একটি সমগ্র কি বের করবেন! রুদ্র খুব চাচ্ছে। খোকা বললেন, অসম্ভব, চাইলেই হবে! আমাকে তো বিক্রির দিকটা দেখতে হবে। যদি সমগ্র না বের করতে চান, তবে অন্তত রাজনৈতিক কবিতা, প্রেমের কবিতা এরকম কিছু একটা বের করুন। এতে খোকা রাজি, কিন্তু সমগ্রতে রাজি নয়। আপাতত তাঁকে রুদ্রর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ করি। অন্তত দেখা তো করুন। সাকুরায় রুদ্র আর আমি দুজনই অপেক্ষা করি খোকার জন্য। খোকা আসেন। রুদ্র নিজ মুখে তার ইচ্ছের কথা জানায় খোকাকে। তখন ওই কথাই আবার তুলি, যে কথা তার সমগ্র বের করার ইচ্ছে শুনে বলেছিলাম, ‘তুমি সমগ্র বের করতে চাইছো কেন! সমগ্র তো মরবার পর বের হয়।’ রুদ্র তবু সমগ্র বের করবেই। কয়েকটি ঘণ্টা কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত মিমাংসা কিছু হয় না, খোকা রাজি হন না সমগ্রতে। রুদ্রকে বার বার বলি, ‘বিদ্যাপ্রকাশ থেকে তোমার বই অবশ্যই বের হবে, তবে সমগ্র নয়। অন্য কিছু বের করো।’ অন্য কিছুতে রুদ্রর ইচ্ছে নেই। রুদ্রর ইচ্ছে সমগ্র।
‘আশ্চর্য তুমি কি মরে গেছো নাকি! অন্তত বুড়ো যদি হতে তাহলেও কথা ছিল। কত বয়স! পয়ত্রিশও তো হয়নি। এক্ষুনি তোমার সমগ্র করার ইচ্ছে কেন?’
অনমনীয় খোকা চলে যান। রুদ্রকে বড় বিষণ্ন দেখতে লাগে। রুদ্রর মন খারাপ দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়। সাকুরা থেকে বেরোই আমরা। আমি আর রুদ্র। পথই আমাদের ঠিকানা। ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছি এখন পথের মানুষ। রুদ্রর হাঁটার কষ্ট সারেনি। পথে তাকে বার বার থামতে হয়। ইচ্ছে করে রুদ্রকে নিয়ে রিক্সায় সারা শহর আগের মত ঘুরি। আগের মত টিএসসির মাঠে বসে তুমুল আড্ডা দিই। ঝালমুড়ি আর চা খেতে খেতে কবিতার কবিতায় কথা কই। আগের সেই উতল প্রেমের দিন গুলো আবার ফিরে আসুক। মাঝখানে এই যে বিভেদ, বিচ্ছেদ, বিষাদ, বিরাগ সব এক নিমেষে উড়ে যাক। রুদ্রর শ্যাওলা পড়া বিষণ্ন চোখে চেয়ে বলি, একটি হাত হাতে নিয়ে, ‘তুমি ভেবো না, তোমার সমগ্র বের করার জন্য আবার আমি বলব খোকা ভাইকে।’
রুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ‘রাজি তো হতে চাইছেন না।’
বলি, ‘দেখি, আমি বই দেব এই কনডিশনে রাজি করাতে পারি কী না। মানুষটা ভাল। তাকে আমি বুঝিয়ে বলব যে তোমার বই অবশ্যই বিক্রি হবে। তোমার জনপ্রিয়তা তো কম নয়। লোকে হরদম আবৃত্তি করছে তোমার কবিতা। বিক্রির দিকটাই কি সব প্রকাশক দেখে! কেউ কেউ তো ভাল কিছু, সে কম বিক্রি হলেও ছাপতে চান। খোকা ভাই বাংলাবাজারের অন্য প্রকাশকের মত অত কমার্সিয়াল দিক নিয়ে ভাবেন না। তিনি আজ রাজি না হলেও হয়ত অন্যদিন রাজি হবেন।’
রুদ্র খানিকটা স্বস্তি পায়। আমরা কিছুদূর পাশাপাশি হেটেঁ এরপর দুটো রিক্সা নিয়ে আমাদের ভিন্ন গন্তব্যের দিকে চলে যাই।
সেই চাবুকের রাতে, যে রাতে আমাকে বাড়িঅলার বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, বাড়িঅলার বউ পারুল ভয়ে থরথর কাঁপতে থাকা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন অনেক কিছু, কি করে মিনারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হল, কেন হল। আমি কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি, সাদা দেয়ালের দিকে নির্বাক তাকিয়েছিলাম। পারুল আমাকে বৈঠক ঘরের এক কোণে শুয়ে পড়তে বললেন। শুয়ে দেয়ালের দিকেই তাকিয়ে থেকেছি বাকি রাত। একটি মুহূর্তের জন্যও আমি চোখের পাতা এক করতে পারিনি। আমি কি বোবা হয়ে গিয়েছি! কেন আমি কিছুই বলতে পারছি না। কেন আমি কাঁদতে পারছি না। কেন আমি পাথর হয়ে আছি! কেন আমি চিৎকার করছি না! কেন আমি কোনও দেয়াল ভেঙে দিচ্ছি না! কেন আমি কাউকে গাল দিচ্ছি না! বকুলির কথা মনে পড়েছে। আমি কি বকুলি হয়ে যাচ্ছি! বকুলির মত বোবা! সেই যে বাবা আরমানিটোলায় সাজানো আমার সুখের সংসারটি ভেঙে দিলেন, আমার মেরুদণ্ড ভেঙে দিলেন, সেই থেকে মনে হয় অনেকদিন আমি বোবা হয়ে আছি। আমি কাউকে কিছু বলছি না। নিজের সঙ্গে কোনও কথা হয় না আমার। ভয় লজ্জা আমার কণ্ঠ রোধ করে আছে। আমি হেরে গেছি বার বার। যেন হেরে যাওয়াই আমার নিয়তি। এই সমাজ সংসার আমাকে আমার মত করে বাঁচতে দিচ্ছে না। আমার শক্তি সাহস উদ্দম, আমার অহংকার আমার ক্রোধ সব আমি কোথাও কারও কাছে বন্ধক দিয়ে বসে আছি। সামনের দেয়ালটি মনে হয় পা পা করে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। চারদিকের দেয়ালগুলো এগিয়ে আসছে। মাথার ভেতর থেকে মস্তিস্কগুলো ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বড় বড় করে শ্বাস নিতে চাইছি। যেন হাওয়াগুলো সব বেরিয়ে গেছে ঘরটি থেকে। বার বার নিজেকে বলি, এই বার তুই তোর কথা বল, তোর মত করে কথা বল তুই। অন্যের সুখের জন্য নিজের সর্বনাশ করিস না আর। নিজের দিকে তাকা তুই, নিজেকে একবার একটু ভালবাসতে চেষ্টা কর। অনেক তো হল, আর কত! আর কত সর্বনাশ করবি নিজের! সাদা দেয়ালে চোখ, দেয়ালটি মনে হয় আমার দিকে পা পা করে এগিয়ে আসছে। একটি দেয়াল নয়, চারদিকের সবগুলো দেয়াল এগিয়ে আসছে। আমি এপাশ ওপাশ করছি। কী এক ঘোরের মধ্যে আমি মাথা নাড়ছি। মাথা নাড়ছি আর অস্ফুট কণ্ঠে বলছি, কথা ক বকুলি। বকুলি কথা ক। কথা ক ..
বোবা হয়ে জেগে থাকা রাতটি পার হয়ে যখন ভোরের সূর্য ওঠে, আমি কথা বলি। পারুলকে বলি, এ বাড়ি থেকে যেন মিনারকে চলে যেতে বলেন তিনি, মিনার চলে গেলে আমি বাড়িটিতে ফিরব। পারুল আমাকে বলেছিলেন কোনও একটি মীমাংসা করে নিতে। আমি না বলেছি। বলেছিলেন পুরুষ মানুষ তো এরকম একটু আধটু করেই, আমি যেন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখি আরেকবার। আমি পারুলকে বলেছি, এ আমি ঠাণ্ডা মাথাতেই ভাবছি, আগে যা কিছু করেছিলাম, মাথার ঠিক ছিল না অথবা মাথা গরম ছিল। বাড়িঅলার বাড়ি থেকে সেই ভোরবেলাতেই আমি বেরিয়ে গিয়েছি। আমি আর শান্তিবাগের অশান্তিতে ফিরিনি। পাখির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। পাখি আমার জন্য একটি ঘরে লেখার টেবিল পেতে সাজিয়ে দিল ঘরটি। হাসপাতাল থেকে ফিরে পাখির সঙ্গে কিচির মিচির করে সময় পার হয়। লেখার চেয়ে মানুষের জীবনের গল্প শুনতেই আগ্রহ বেশি আমার। শান্তিবাগের বাড়িতে ভক্ত হিসেবে আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, সেই থেকে আসা যাওয়া করতে করতে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে পাখির সঙ্গে। পাখি দশ তলার একটি অ্যাপার্টমেণ্টে থাকে। একা থাকে। স্বামীর সঙ্গে তালাক হয়ে গেছে। প্রাক্তন স্বামীটি থাকে আমেরিকায়। পাখি দেখতে সুন্দরী, এমন রং মেখে মুখের ভাঁজ ঢেকে রাখে যে বয়স বোঝার উপায় থাকে না। পাখি অনেকটা মা মা, অনেকটা বোন বোন। পাখি তার জীবনের সব গল্প অকপটে আমার সঙ্গে করে। পাখির একটি মেয়ে আছে, মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে, থাকে আরব দেশে। পাখি একা থাকে ঢাকায়। অবশ্য নিজের উপার্জন তেমন কিছু নেই। মাঝে মধ্যে এটা ওটা সেলাই করে বিভিন্ন কাপড়ের দোকানে সেসব বিক্রি করার চেষ্টা করে। স্বামীর সঙ্গে তালাক হওয়ার পর ঢাকার পল্লবীতে একটি বাড়ি ছিল, স্বামী কিনেছিল স্ত্রীর নামে, সেটি সে বিক্রি করে বড় এই অ্যাপার্টমেন্টটি কিনেছে। বাকি টাকা ব্যাংকে। একা থাকা পাখির যে মনের শক্তি, সেটি আমাকে মুগ্ধ করে। পাখি নাকি আমার লেখা পড়ে একা থাকার সাহস আর শক্তি পেয়েছে। আমার লেখা যে মানুষকে এমন শক্তি যোগায় তা আমার জানা ছিল না। কুষ্টিয়া থেকে পাখির বড় বোন এসেছিলেন, তিনিও আমার লেখা পড়েন। আমাকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি আমাকে দেখছেন। জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন বুকে। লাগামছাড়া প্রশংসার সামনে আমি কিংকর্তব্যবিমুঢ়ের মত বসে থাকি। লেখা পড়ে আমাকে যে রকম ভাবে মানুষ, আমি সাংঘাতিক সাহসী, পুরুষ টুরুষ একেবারেই পছন্দ করি না, পুরুষ দেখলে গালে চড় কষিয়ে দিই, তলপেটে লাথি মেরে শুইয়ে দিই, অথচ মোটেও সেরকম নই দেখে, কেউ কেউ হয়ত অবাক হয়, আহত হয়। মুর্ছা যাবে যদি জানে আমাকে পুরুষের চাবুক খেতে হয়। পাখি এমন ভক্ত আমার, এই পাখির বাড়িতেও আমার আশ্রয়হীনতার অসহায়ত্ব নিয়ে অস্বস্তি হয়। আমি লক্ষ্য করি পাখি আমাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তার বাড়িতে থাকার কথা বলে না। বলে না যতদিন না আমি নিজের জন্য একটি ঘর পাই, ততদিন তার বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করে আমি থাকতে পারি। আমারও ইচ্ছে করে না পাখির কাছে করজোড়ে আরও কয়েকটি দিন ভিক্ষে চাইতে। পাখির বাড়িতে থাকার নির্দিষ্ট সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসে।
ঢাকা শহরে অনেক বন্ধু, বান্ধবী, অনেক আত্মীয় স্বজন, কিন্তু এ সময়, আমি জানি, কেউ আমাকে পেয়ে খুশিতে বাগবাগ করবে না। পাখির বাড়ি থেকে বিদেয় হওয়ার পর আশ্রয়হীন আমি হোটেলে থাকার সিদ্ধান্ত নিই। গুলিস্তানের একটি হোটেলে আমার জীবন শুরু হয়। রেস্তোরাঁয় খাওয়া। সারাদিন হাসপাতালে, রাতে ঘুমোনোর জন্য হোটেলে ফেরা। হোটেলে থাকা সহজ ব্যপার নয়। ঘিঞ্জি এলাকায় শহরের সস্তা হোটেলগুলোয় কোনও পুরুষই কোনও মহিলা-আত্মীয় নিয়ে ওঠে না। হোটেলের ম্যানেজারও চোখ কপালে তুলেছিলেন আমি থাকব শুনে। আবারও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন খোকা। সুসময়ে অনেকেই আসে কাছে। দুঃসময়ে খুব বেশি মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। আমার দুঃসময়ে খোকা সত্যিকার ভাইএর মত, বাবার মত, বন্ধুর মত পাশে থাকেন। আমার নিদারুণ নিরূপায় অবস্থা দেখে আর কারও মত আমাকে স্পর্শ করার কোনও সুযোগ খোঁজার চেষ্টা করেন না। খোকা হোটেলের ম্যানেজারকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলেছেন, ‘মা বোন তো সবারই আছে, কি কন! তাদের অসুবিধা তো আমাদের দেখতে হবে। উনি হচ্ছেন ডাক্তার, মিটফোর্ডে চাকরি করেন। আপাতত থাকার অসুবিধে বলে হোটেলে কদিন থাকতে হবে।’ ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত রাজি হন। কেবল রাজিই নন, রাতে আমার ঘরের দরজায় কোনও রকম উৎপাত যেন না হয় সে দিকে কড়া নজরও রাখেন। তবু ঘরের ভেতর বেশির ভাগ রাতেই আমার ঘুম হয় না। দরজা কেউ লাথি দিয়ে ভাঙতে চাইলে ভেঙে ফেলতে পারে। মাতাল বদমাশদের আড্ডাখানা হোটেল, নিশ্চিত হই কী করে! হোটেল জীবনের অবসান ঘটে যখন শান্তিবাগের বাড়িঅলা জানান যে মিনারকে তারা বাড়ি থেকে নোটিশ দিয়ে বের করেছেন। মিনার তার জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে। বাড়িটিতে উঠে আমার আবার আগের সেই আনন্দ ফিরে পাই। আরমানিটোলার বাড়িতে যেমন সুখের সংসার গড়েছিলাম, তেমন একটি সংসারের স্বপ্নে আবার আমি বিভোর হই। খালি বাড়ির মেঝেয় শুয়েই সুখনিদ্রা যাই। নিজের ওপর যে বিশ্বাস টুকু হারিয়েছিলাম, সেটি নিঃশব্দে, আমাকেও বুঝতে না দিয়ে ফিরে আসে। নিজেকে আর দীন হীন কীট সম কিছু মনে হয় না।
১১. দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি
দুপুরে অসীম সাহা হাসপাতালে ফোন করে খবর দেন রুদ্র অসুস্থ, হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের দুশ একত্রিশ নম্বর কেবিনে ভর্তি। খবরটি শুনে আমি আর দেরি করিনি, একটি রিক্সা নিয়ে সোজা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের দিকে যাই। হাসপাতালের গেটের কাছে ফুলের দোকানে নেমে একগোছা রজনীগন্ধা কিনি। রুদ্রর খুব প্রিয় ফুল রজনীগন্ধা। হাসপাতালের নার্সের ঘরে গিয়ে একজন নার্সকে অনুরোধ করি দুশ একত্রিশ নম্বরে গিয়ে আমার নামটি রুদ্রকে বলতে, রুদ্র অনুমতি দিলে আমি ভেতরে ঢুকবো। ভেতরে রোগী দেখার অনুমতি হয়ত সবাই পায় না। আমি পাবো সে ব্যপারে আমি নিশ্চিত নই। রুদ্রর ঘরে রুদ্র ছাড়াও অন্য কেউ থাকতে পারে, আমার উপস্থিতি হয়ত পছন্দ করবে না। নার্স একবার বলেছিল, আপনি সোজা চলে যান রুমে। সোজা চলে যাওয়ার চেয়ে অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত বলে আমি অপেক্ষা করি। অনুমতি মেলে। আমি জানি, অন্য কেউ না বললেও রুদ্র আমার নাম শুনলেই দেখা করতে বলবে। রুমে রুদ্রর তিনটে বোন ছিল, কারও সঙ্গে কোনও কথা হয়নি, কথা কেবল রুদ্রর সঙ্গেই হয়েছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বলেছে, ‘বসো’।
রজনীগন্ধাগুলোর ঘ্রাণ নেবে কী! নাকে নল। ফুলগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিই। শিয়রের কাছের চেয়ারটিতে বসে জিজ্ঞেস করি, ‘কী হয়েছে তোমার?’
‘ডাক্তার বলল পেটে নাকি আলসার।’ রুদ্র মাথা নাড়ায় না। কেবল চোখ নাড়িয়ে এপাশ ওপাশ তাকায়। মুখটি বড় মলিন।
‘পেটের আলসার এমন কোনও ব্যপার নয়। সেরে যাবে।’
‘সেরে যাবে?’
‘নিশ্চয়ই। এ রোগ শতকরা আশি জনের হয়। এ কোনও রোগ হল!’
‘নাকে নল নিয়ে তোমাকে লাগছে কেমন বলো তো!’ আমি মুচকি হাসি।
আমার ডানহাতের আঙুলগুলো রুদ্রর চুলে বিলি কাটছে। বাম হাত তার বুকে।
‘কষ্ট হচ্ছে?’
‘কষ্ট তো হচ্ছেই।’
‘একটুও ভেবো না। তুমি খুব শিগরি ভাল হয়ে উঠবে।’
‘কী জানি! এ যাত্রাই শেষ যাত্রা কি না।’
‘বাজে কথা বলো না।’
এরপর রুদ্র মৃদু স্বরে কে কে তাকে দেখতে এসেছিল, কোন কোন কবি লেখক, কি কি বলেছে তারা, কি কি করেছে, বলে। বলে শিমুলের কথাও।
‘আজই এসেছিল। চুপচাপ বসেছিল। মুখ ভার।’
‘কেন, ভার কেন?’
‘বোধহয় আমার এই অবস্থা দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে। কোনও কথাই বলেনি।’
‘বিয়ে করছো কবে?’
‘যদি সুস্থ হই..’
‘সুস্থ তো নিশ্চয়ই হবে।’
শিমুলের কথা যখন বলে রুদ্র তার মলিন মুখটি উজ্জ্বল দেখায়। বুঝি, শিমুলকে খুব ভালবাসে রুদ্র। অনেকক্ষণ শিমুলের কথাই বলে সে।
‘দূরে বসেছিল। কাছে এসে বসতে বলেছে, কাছে আসেনি।’
‘কেন আসেনি?’
‘রাগ করে আসেনি। অসুখ বাঁধিয়েছি বলে রাগ করেছে।’
‘ভাল, ওর হাতে পড়লে তোমার অনিয়ম করা চলবে না।’
রুদ্রর উজ্জ্বল মুখে হাসি। আমিও হাসতে চেষ্টা করি। যেন রুদ্রকে অন্যের হাতে সঁপে দিতে আমার মোটেও কষ্ট হচ্ছে না।
রুদ্রর সঙ্গে কখনও আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোনও কথা হয়নি। সম্ভবত লোকের কাছে শোনে সে। আমি একা থাকি নাকি কারও সঙ্গে থাকি, ভাল আছি কী ভাল নেই — কিছু সে কোনওদিন জানতে চায়নি। নিজের কথা বলে সে। নিজের প্রেমের কথা। নিজের কবিতার কথা। অসুখের কথা। সুখের কথা।
‘শিমুলকে নিয়ে লিখলে কিছু,কোনও কবিতা?’
‘হ্যাঁ।’ রুদ্র ধীরে মাথা নাড়ে।
‘কাছে নেই?’
‘কাছে! হাসপাতালে!’ রুদ্র ম্লান হাসে।
‘নয় কেন! তোমার কবিতার খাতা তো সঙ্গে থাকেই তোমার! সে যেখানেই যাও।’
‘আর বোলো না। এই হাসপাতাল থেকে জলদি বেরোতে পারলে বাঁচি।’
‘অস্থির হয়ো না। আগে সুস্থ হও, তারপর বাড়িতে তো যাবেই। খাবারের আগে পরে খাওয়ার জন্য ডাক্তার কিছু ওষুধ লিখে দেবে। সেসব খেও নিয়মিত। পকেটে এন্টাসিড ট্যাবলেট রাখবে বাইরে গেলে। এসিডিটির ভাব দেখলে খেয়ে নেবে।’
‘ডাক্তার বলেছে ব্লাড প্রেশার বেশি।’
‘ব্লাড প্রেশার বেশি? বল কি! এই বয়সে ব্লাড প্রেশার বাড়বে কেন! ঠিক দেখেছে ডাক্তার?’
‘বলল তো!’
‘তাহলে তোমাকে খুব সাবধান থাকতে হবে। প্রেশার কমার ওষুধ দিচ্ছে তো!’
‘দিচ্ছে।’
‘কি বলল? সিগারেট মদ সব আগের মত চালিয়ে যেতে বলেছে?’
‘এবার বোধহয় সব ছাড়তেই হবে।’
‘ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও। নিয়মিত খাওয়া দাওয়া কোরো, দেখবে পেটের অসুখে আর ভুগতে হবে না।’
সেদিন কথা দিয়েছিলাম আবার তাকে দেখতে যাবো। সেই দেখতে যাওয়া আর হয়নি। এরপর তো ইয়াসমিন এল শান্তিবাগের বাড়িতে, মিলন এল। মিলন ঢাকায় এসেছে চাকরি করতে। বাসাবোর এক গলিতে তার বোনের বাড়িতে ছিল, এখন এ বাড়িতে নিয়ে এসেছি। এতদিন বিয়ের কলংক নিয়ে মুখ লুকিয়েছিলাম। অবকাশে যাইনি। আত্মীয় স্বজন কারও সঙ্গেই দেখা করিনি। পূর্বাভাস পত্রিকায় আমার কলামের সমালোচনা করতে গিয়ে এক লোক লিখেছিল, যার এক কান কাটা সে কাটা কানটি আড়াল করতে রাস্তার এক কিনার দিয়ে হাঁটে, আর দুই কান কাটা যার, সে রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে হাঁটে, কারণ তার আড়াল করার কিছুই নেই, আমি কাটা দুটো কান নিয়ে নির্লজ্জের মত রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে হাঁটছি। আমি নির্লজ্জ বলে এমন আবোলতাবোল কথা লিখছি কলামে। আমাকে অপদস্থ করার জন্য লেখাটি। হেনস্থার যেহেতু শেষ নেই, রাস্তার মধ্যিখান দিয়েই হাঁটব পণ করেছি। একাধিক বিয়ের লজ্জা, দুর্নামের ভয় ইত্যাদি নিয়ে মুখ লুকিয়ে থাকলে আর কারও লাভ হয় হয়ত, আমার কিছু হয় না।
ইয়াসমিনকে নিয়ে ছোটদার বাড়িতে গিয়েছি সুহৃদকে দেখতে, তখনই ও বাড়িতে আমার ফোন এল। ও বাড়িতে আমার ফোন, অবাক কাণ্ড বটে। হ্যাঁ ওটি আমারই ফোন। করেছে ক্যারোলিন রাইট। ক্যারোলিন রাইট আমেরিকার কবি, এখানে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে বাঙালি মহিলা কবিদের কবিতা নিয়ে গবেষণা করতে এসেছে। আমার কবিতার ওপরও তাঁর গবেষণা চলছে, অনুবাদও কয়েকটি কবিতার করেছে। ক্যারোলিনের সঙ্গে দুদিন দেখা হয়েছে বাংলা একাডেমিতে যখন সে মুহম্মদ নুরুল হুদার সাহায্য নিয়ে আমার কবিতা অনুবাদ করছিল। ক্যারোলিনকে যে আমার খুব পছন্দ হয়েছে তা নয়। কিছুদিন এখানে থেকেই ভাব এমন যে এখানকার রাজনীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি, সাহিত্য সংস্কৃতি সবই তার নখদর্পণে। এর মধ্যেই সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের প্রেমে পড়ে গেছে, মঞ্জুরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ক্যারোলিনকে সাহায্য করছিলেন অনুবাদে। ক্যারোলিন যে কারও শোবারঘরে বড় নাক গলাতে চায়। আমি কটি বিয়ে করেছি, কাকে বিয়ে করেছি, ইত্যাদি জানার জন্য ক্যারোলিনের উৎসাহ টগবগ করে। বিদেশি মেয়ে, ধারণা ছিল কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামায় না। দেখলাম, কবিতার চেয়ে কবি নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহ তার বেশি। চরিত্র অবিকল গুঁজাবুড়ি কুটনিবুড়ির। পরে এই ক্যারোলিনকেই, যেহেতু সে সুন্দর বাংলা শিখেছে, একদিন টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে তার কবিতা পড়ার সুযোগ করে দিই। টেলিভিশন থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, আমি প্রযোজিকাকে বলে কয়ে ক্যারোলিনকে ঢুকিয়েছি অনুষ্ঠানে। ক্যারোলিন সে কী খুশি! চশমা পরলে তাকে নাকি কুৎসিত লাগে তাই চশমা খুলে ক্যামেরার সামনে এসেছিল। চশমা ছাড়া কাগজ দেখে নিজের লেখা পড়তেও তার অসুবিধে হচ্ছিল, তবু সে চশমাটা পরে নেয়নি, এমন। চশমা জিনিসটি আমার এত ভাল লাগে যে ছোটবেলায় চশমা পরার জন্য মধ্যাহ্নের সূর্যের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতাম, চোখের ভেতর খোঁচাতাম যেন চোখ নষ্ট হয়, যেন বাবা আমাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান, যেন চোখের ডাক্তার আমার চোখ পরীক্ষা করে বলেন যে আমার চোখ নষ্ট, যেন একটি চশমা আমাকে দেন পরতে। ক্যারোলিন সেদিন ফোনের ওপাশ থেকে ভাঙা বাংলায় বলল, ‘রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ মারা গেছে, তুমি জানো?’
‘কি বললে?’
‘রুদ্র মারা গেছে।’
‘রুদ্র মারা যাবে কেন?’
‘আজ সকালে মারা গেছে।’
‘পাগলের মত কথা বলছো কেন! আমি তো সেদিন মাত্র রুদ্রকে দেখে এলাম হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে। মরে যাওয়ার মত কোনও অসুখ ওর হয়নি।’
‘কিন্তু আমি শুনলাম মারা গেছে।’
‘তোমাকে কে বলেছে এসব কথা?’
‘বলেছে একজন। একজন কবি।’
‘নাম কি? যদি বলে থাকে মিথ্যে বলেছে ।’
‘কিন্তু সে কবিটি মিথ্যে বলবে না। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো।’
‘শোনো ক্যারোলিন,রুদ্র হাসপাতালে এই কথাটি হয়ত তোমাকে বলেছে, তুমি শুনতে ভুল করেছো।’
‘আমাকে ষ্পষ্ট বলল মারা গেছে।’
‘তাহলে যে বলেছে সে জানে না। কারও কাছে হয়ত শুনেছে যে রুদ্রর অসুখ। বানিয়ে বানিয়ে বলে দিল মারা গেছে। কানে কানে কত রকম খবর যে পৌঁছোয়।’
‘যাই হোক, তুমি খবর নিও।’
ক্যারোলিনের খবরটিকে সত্য মনে করার কোনও কারণ আমি দেখিনি। তবু ইয়াসমিনকে নিয়ে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে যাই। হাসপাতালে রুদ্র যে কেবিনে ছিল সে কেবিনে খোঁজ নিয়ে দেখি রুদ্র নেই। নার্সকে জিজ্ঞেস করলে বলল, ‘রোগী গতকাল বাড়ি চলে গেছে।’
‘সুস্থ হয়েছিল?’
‘হ্যাঁ হয়েছিল।’
‘পুরোপুরি সুস্থ হয়েছিল, নাকি রোগী এখানে থাকতে চায়নি বলে নাকে নল টল নিয়ে বাড়ি চলে গেছে।’
নার্স আমার দিকে বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলে, ‘সুস্থ না হলে কি ডাক্তার ডিসচার্জ দেয় নাকি?’
নার্স রুদ্রর ফাইল বের করে আমাকে দেখিয়ে বলল, ‘রোগী ভাল হয়ে গেছে, ডাক্তার তাই বাড়ি চলে যেতে বলেছে।’
হলি ফ্যামিলি থেকে রিক্সায় উঠে গজরাতে থাকি। ‘মানুষের মুখের কোনও লাগাম নাই। যা ইচ্ছ! তাই বইলা ফালায়। রুদ্র ভাল হইয়া দিব্যি হাসপাতাল থেইকা বাসায় গেছে । আর মানুষে কয় যে মারা গেছে।’ বলি কিন্তু রিক্সাঅলাকে বলি ইন্দিরা রোডের দিকে যেতে।
ইয়াসমিন বলে, ‘ইন্দিরা রোডে যাইবা কেন?’
‘দেখি গিয়া। রুদ্র বাসায় ঠিক মত গেছে এইডা একটু কনফার্ম হইয়া আসি। অবস্থা খারাপ হইলে তো নার্সই কইত।’
জানি খবরটি সত্য নয়, তবু সারা রাস্তা আমি অন্যমন বসে থাকি। ইয়াসমিন বলে, ‘কি চিন্তা কর? কিছু ত হয় নাই। এমনি একটা গুজব।’
‘গুজবই আসলে।’
‘কী অসুখ ছিল? হাসপাতালে ছিল কেন?’
‘বেশি কিছু না। পেটের আলসার ছিল। আমি দেইখা গেলাম সেইদিন। ভাল ট্রিটমেন্ট চলতাছিল। মারা যাবে কেন? মারা যাওয়ার তো কোনও কারণ থাকতে হবে। যে মানুষ হাসপাতাল থেইকা আলসারের ট্রিটমেন্ট পাওয়ার পর সুস্থ হইয়া বাসায় যায় গা, সেই মানুষ নাকি মারা গেছে। এর মত আজগুবি কথা আরও আছে? যদি কোনও কঠিন অসুখ হইত, বুঝতাম।’
ইন্দিরা রোডে যাচ্ছি কিন্তু রুদ্রর বাড়ির ঠিকানা জানি না। ঝিনাইদহ থেকে যে রাতে এসেছিলাম, পথ আবছা যেটুকু মনে আছে, অনুমান করে এগোতে থাকি। হঠাৎ দেখি এক গলিতে চার পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। এরমধ্যে দুজনকে চিনি, একজন মইনুল আহসান সাবের। বুকের ভেতর হঠাৎ ভীষণ ঝড়ো হাওয়া এসে যা কিছু ছিল বুকে সব ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মুহূর্তে রক্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শরীরে কাঁপুনি ওঠে। অন্ধকার লাগে সামনের সব কিছু। চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে নিজের এই কাঁপনকে রোধ করতে করতে বলি, ‘ইয়াসমিন রুদ্রর বন্ধুরা এইখানে কেন! কী হইছে?’
ইয়ামমিন কোনও কথা বলে না।
‘তাইলে কি সত্যি খবরটা?’
ইয়াসমিন কোনও কথা বলে না।
রিক্সা এগোতে থাকে। আরও মানুষের জটলা, আরও চেনা মুখ।
‘না, খবরটা সত্যি হইতে পারে না। অসুখ বোধহয় বেশি।’
আমি সান্ত্বনা খুঁজি। ইয়াসমিনের হাত চেপে ধরে রাখি।
‘ক কথা ক। ঠিক না!’
ইয়াসমিন কোনও কথা বলে না।
‘এত মানুষ কেন! সবাই ইন্দিরা রোডে কেন! কোনও কবিতার অনুষ্ঠান আছে বোধহয় এই গলিতে! নাকি রুদ্রর কাছে আইছে তারা! কিন্তু এত মানুষ আইব কেন?’ চাপা আর্তনাদ আমার কণ্ঠে।
ইয়াসমিন তার হাতটি আমাকে শক্ত করে চেপে রাখতে দেয়। কোনও কথা বলে না। যে বাড়িটির সামনে লোকের ভিড়, সেই বাড়ির কাছে রিক্সা থামিয়ে নেমে ভিড় সরিয়ে দৌড়ে দোতলায় উঠি আমি। ঘরের দরজা খোলা, কান্নার শব্দ ভেসে আসছে ভেতর ঘর থেকে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন অসীম সাহা।
‘অসীম দা, কী হয়েছে?’ বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, ‘নাসরিন, রুদ্র নেই।’
‘কি বলছেন এইসব!’
শরীর থেকে শরীরের সব শক্তি কর্পুরের মত উবে যায়। শরীরটি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, পেছনের দেয়ালে ভর রেখেও শক্তিহীন শরীরটিকে আমি দাঁড় করাতে পারি না। পালকের মত এটি নিচে পড়তে থাকে। পুরো জগতটি লাটিমের মত ঘুরতে থাকে, শব্দহীন হয়ে যেতে থাকে সব। নিজের গলা ছেড়ে কাঁদার বা গোঙানোর বা কাতরানোর কোনও শব্দও আর শুনতে পাই না। অসীম সাহার কান্নার শব্দও আমার কানে আর পৌঁছে না। চারদিকের মানুষগুলোর মুখগুলোও আমার আর চেনা মনে হতে থাকে না। মানুষগুলো জলের ভেতরে নানারকম আকার নিয়ে ভাসতে থাকে। যেন মাছ সবাই। আমি একটি মৃত ডাল পড়ে আছি জলের তলে। মাছগুলো নিঃশব্দে সাঁতার কাটছে। ওভাবে কতক্ষণ পার হয় জানি না। চলতে চলতে হঠাৎ স্থির হয়ে আছে সময়। ঘড়ির কাঁটা হয়ত কোথাও টিক টিক করে চলছে, জগত হয়ত যেমন চলছিল, তেমন চলছে, আমার জগতে স্থির সময়ের মত সবকিছুই নির্বাক নিথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। আমি আমাকে আর আমার ভেতর অনুভব করি না। আমি আর কিছুই অনুভব করি না। কেউ আমাকে স্পর্শ করলেও না। কেউ আমাকে ডাকলেও না।
একটি মাছ এগিয়ে আসে মৃত ডালের দিকে। প্রজ্ঞা লাবণীর আকার ধরে মাছটি আমাকে স্পর্শ করে। স্পর্শটি আমাকে কোথাও কোনও মাছের বাজারের ভীষণ কোলাহলের মধ্যে টুপ করে ফেলে দেয়। আমি মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি চারদিকের দরদামের চিৎকার, ঘামের গন্ধ আর এক ঘর নোংরার মধ্যে। আশ্চযর্, সব কিছুর মধ্যে, মেঝেয় শুয়ে কী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে রুদ্র। কোনও দুর্গন্ধ, কোনও কোলাহল তাকে জাগাচ্ছে না। রুদ্র, সেই রুদ্র, আমার ভালবাসার রুদ্র, দিবস রজনী আমি যার আশায় আশায় থাকি। ঘুমিয়ে আছে রুদ্র। একটি রেখা রেখা সাদা চাদরের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে রুদ্র। এই চাদরটিতে দুজন শুয়েছি আমরা কত রাত। কত রাত আমাদের আনন্দ রসে ভিজেছে এই চাদর। কত রাত এই চাদরের যাদু আমাদের সাত আসমান ঘুরিয়ে এনেছে। কত রাত আমার সারা শরীরে চুমু খেতে খেতে আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে এই চাদরে ঘুমিয়েছে রুদ্র। এখন সে পুরো চাদর জুড়ে স্বার্থপরের মত একা শুয়ে আছে। আমাকে পাশে শুতে ডাকছে না। যেন রুদ্র শোনে, কেবল সে-ই শোনে শুধু, এমন নিভৃতে, প্রায় কানে কানে বলি ‘এই, এখন কি ঘুমোবার সময়! ওঠো। দেখ আমি এসেছি। চল কোথাও বেরিয়ে পড়ি। এখানে এত লোক! চল দুজন চুপ চুপ করে আলাদা হয়ে যাই। সেই আগের মত, ভিড় থেকে বেরিয়ে সেই যে চলে যেতাম কোথাও! হন্যে হয়ে নির্জনতা খুঁজতাম। ওঠো। না হয় না গেলে কোথাও, উঠে বসো তো বাবা, কবিতা শোনাও, নতুন কি লিখেছো, শোনাও। তোমার কোলে মাথা রেখে শুনব কবিতা। চমৎকার আবৃত্তি করে মুগ্ধ করে দাও সবাইকে।’
রুদ্র ওঠে না। মিহি সুরে একটি কান্নার শব্দ শুনি, কান্নার কণ্ঠটি হঠাৎ কথা বলে ওঠে, ‘কী দেখতে এসেছো তুমি! কারে দেখতে এসেছো! দেখে যাও! দেখে যাও! প্রাণ ভরে দেখে যাও আমার ছেলেরে। কম কষ্ট তো দাওনি ওরে। দেখতে এসেছো এখন!’ পাথরের মত পার্থিব জগতটিতে দাঁড়িয়ে থাকি রুদ্রর পাশে। জগতের অশ্লীল শব্দগুলো আমাকে খোদাই করছে। শব্দ ভেসে আসছে লাশ ওঠাও, লাশ নামাও। রুদ্রকে রুদ্র না বলে ওরা লাশ বলে সম্বোধন করছে ! আহ রুদ্র, চোখ খোলো, দেখ, মোহন রায়হান তোমাকে লাশ বলে ডাকছে। মনে আছে, মেরে তোমার লাশ ফেলে দেবে বলেছিল যে ছেলেটি! দেখ, মুখে কেমন ফেনা তুলে ফেলছে তোমাকে লাশ ডাকতে ডাকতে। রাগ হচ্ছে না তোমার! আমি জানি না কখন পাথরটিকে কে সরিয়ে নিয়ে রিক্সায় তুলে দেয়। রিক্সা যাচ্ছে ট্রাকটির পেছন পেছনে, ট্রাকে রুদ্র। রুদ্র এখন টি এসসিতে যাবে। ওখান থেকে মিঠেখালি।
‘কি হইছে রুদ্রর?’ পাথর গলে যেতে থাকে।
‘সকালে ঘুম থেইকা উইঠা দাঁত মাজতে গেছিল। দাঁত মাজতে মাজতে হঠাৎ পইড়া গেছে। হার্ট এ্যাটাক।’
‘বাজে কথা কইস না। ইয়াসমিনকে ধমকে থামাই। ইয়াসমিন চুপ হয়ে যায়।
অনেকক্ষণ পর ধীরে আমি, এই জগতে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, ‘ইয়াসমিন, রুদ্র কি সত্যিই মারা গেছে?’
ইয়াসমিন কথা বলে না।
‘কথা ক। কথা ক ইয়াসমিন। সত্যি কইরা ক, ক যে মারা যায় নাই। ওর হার্ট এ্যাটাক হইব কেন? হার্টের তো কোনও প্রবলেম ছিল না ওর। ক যে মারা যায় নাই। ক যে ও ঘুমাইয়া রইছে।’
ইয়াসমিন কথা বলে না।
না, কোথাও কিμছু হয়নি। আমি আর ইয়াসমিন ঘুরে বেড়াচ্ছি ঢাকা শহরে। ইয়াসমিনের সঙ্গে আমার অনেকদিন পর দেখা। দুজন আমরা ময়মনসিংহের রাস্তায় যেমন ঘুরে বেড়াতাম, তেমন ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও যাইনি আমরা, কোনও ইন্দিরা রোডে যাইনি, কিছুই দেখিনি। রিক্সায় বসে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যেস আমার আছে, ঘুমিয়ে থাকার সময় কোনও দুঃস্বপ্ন দেখেছি হয়ত। কলকল করে উঠি সুখী স্রোতের মত, রিক্সার হুড ফেলে দিয়ে, ‘চল বেইলি রোডে যাই, শাড়ি কিনি গা।’
‘না।’
‘না কেন!’
‘বাসায় চল।’
‘কিসের বাসা! বাইরইছি ঘুরতে। চল ঘুইরা বেড়াই।’
‘না, বাসায় চল বুবু।’
অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থেকে রিক্সাকে বলি টিএসসির দিকে যেতে। ইয়াসমিন বলে, ‘টিএসসিতে যাইও না।’
ইয়াসমিনকে জোরে ধমক লাগাই চুপ থাকতে। ধমকে ইয়াসমিন চুপ হয় না। আমাকে জাপটে ধরে ভাঙা গলায় বলে, ‘বুবু, তুমি এমন কইর না।’
‘চল টিএসসিতে যাই। ওইখানে রুদ্র আছে।’
‘না।’
‘আমি রুদ্রর কাছে যাবো।’
‘বুবু, থামো এইবার। ওরা কেউ তোমারে পছন্দ করতাছে না। তুমি যাইও না টিএসসিতে।’
আমি বিশ্বাস করতে চাই যে রুদ্র নেই। নিজেকে বার বার বলি রুদ্র নেই। রুদ্র আর নেই। রুদ্রর শরীর পড়ে আছে শুধু। সেই শরীরে হৃদপিণ্ডটি থেমে আছে, কোনও রক্ত সেখানে যাচ্ছে না, সেখান থেকে বেরোচ্ছে না, হৃদপিণ্ডের কোনও সংকোচন প্রসারণ হচ্ছেন!। রক্ত বইছে না শরীরে।ফুসফুস দুটো স্থির হয়ে আছে। রুদ্র শ্বাস নিচ্ছে না, ফেলছে না। রুদ্র আর জেগে উঠবে না। রুদ্র আর কবিতা লিখবে না। রুদ্র আর হাসবে না। রুদ্র আর কোনও মঞ্চে কবিতা পড়বে না। সবাই যার যার জীবন যাপন করবে, কেবল রুদ্র করবে না। বিশ্বাস করতে চাই, কিন্তু পারি না। আমার কিছুতে বিশ্বাস হয় না, রুদ্র সত্যি সত্যি নেই। রুদ্র নেই, এ কথা যখনই ভাবি, শকুন খেয়ে যাওয়া গরুর পাঁজর যেমন পড়ে থাকে বধ্যভূমিতে, আমার পাঁজরও অনুভব করি তেমন। খালি। ভেতরে কিছু নেই। হু হু করছে চারদিক, হু হু করছে বুকের ভেতর। শ্বাস নিতে চেষ্টা করি, কষ্ট হয়, যেন বাতাস ফুরিয়ে গেছে, পৃথিবীর সকল বাতাস। চারপাশের মানুষগুলো মানুষ নয়, সব শকুন। আমার চোখের কোটরে চোখ নেই। আমার খুলির ভেতর মস্তিস্ক নেই। সব খেয়ে গেছে কেউ। এই অনুভবটি আমার সমস্ত শরীরে সংক্রামক ব্যধির মত ছড়িয়ে যায়। রিক্সা কখন থেমেছে শান্তিবাগের বাড়িতে বুঝিনি, কখন উঠে এসেছি ঘরে, কখন দেয়ালে হেলান দিয়ে একা বসে আছি বুঝিনি। কতক্ষণ কত দীর্ঘক্ষণ বসে আছি কিছুই জানি না। হঠাৎ কাঁধে একটি হাত অনুভব করি কারওর, গভীর শূন্যতা থেকে চোখ উঠিয়ে দেখি নাইম। তখনই বাঁধ ভেঙে উতল সমুদ্রের জল নামে, ভাসিয়ে দেয় স্তব্ধ চরাচর।
আমার পক্ষে ঢাকায় এক মুহূর্তের জন্য থাকা সম্ভব হয় না। ঢাকা যেন আচমকা আস্ত একটি শ্মশান হয়ে গেছে। শ্মশানে কোনও মানুষের চিহ্ন নেই। বাতাসে লাশের গন্ধ। ছোটদা খবর পেয়ে গাড়িতে মাল ওঠান। সপরিবার তিনি রওনা হন ময়মনসিংহে। আমি গাড়ির জানালায় মুখ রেখে দেখছিলাম গাছপালা ক্ষেত খামার। সবই তো যেমন ছিল, তেমনই আছে। কেবল রুদ্র নেই। রুদ্র আর হাঁটবে না কোনও পথে, আর ঘ্রাণ নেবে না কোনও ফুলের, আর নদীর রূপ দেখবে না, ভাটিয়ালি গান শুনবে না। আমার বিশ্বাস হয় না রুদ্র আর হাঁটবে না, ঘ্রাণ নেবে না, দেখবে না, শুনবে না। কেন যেন মনে হয় রুদ্র ফিরে আসবে। আবার হঠাৎ করে ফিরে আসবে একদিন। বলবে ‘মিঠেখালি গিয়েছিলাম, আজ ফিরেছি।’ যেমন ফিরে আসত বার বার। আমি কোনও অলৌকিকে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে ভাল লাগে যে রুদ্র ফিরে আসবে। আবার হাসবে, লিখবে,ভাববে, ভালবাসবে।
ঢাকা শ্মশান শ্মশান লাগছিল বলে ময়মনসিংহে ফিরে দেখি এটিও শ্মশান। বিছানার তল থেকে আমার ট্রাংকটি টেনে এনে খুলি। রুদ্রর স্পর্শ পেতে খুলি। যে করেই হোক রুদ্রর স্পর্শ চাই আমি। তাকে আমি স্মৃতি হতে দিতে চাই না। রুদ্রর চিঠিগুলো পড়তে পড়তে পুরোনো দিনগুলো চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। দিনগুলো আমার এত কাছে যে আমি দিনগুলোকে স্পর্শ করি। দিনগুলোতে ভাসি, ডুবি, দিনগুলো নিয়ে খেলি, দিনগুলোকে চুলে বিনুনির মত বেঁধে রাখি। দিনগুলো হঠাৎ ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে যখন কেউ আমাকে ডাকে। তাহলে সেই দিনগুলো নেই! সেই ভালবাসার দিনগুলো! সবই কেবল স্মৃতি! ভয়ংকর রকম নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে, ভয়ংকর রকম একা। নিজেকে সামনে নিয়ে বসে থাকি, এ জীবন নিয়ে কি করব আমি বুঝি না, মূল্যহীন মনে হতে থাকে জীবনটি। যে মানুষটি আমাকে ভালবাসত, সেই মানুষটি নেই! যে মানুষটির জন্য কতকাল আমি স্বপ্ন দেখেছি, নেই! যে মানুষটিকে ছেড়েছি, কিন্তু ছাড়িনি; যে মানুষটি থেকে দূরে সরেছি, কিন্তু দূরে সরিনি, সে নেই। এই নেই টি আমাকে বাড়ি কাঁপিয়ে কাঁদায়। পাড়া কাঁপিয়ে কাঁদায়। কালো ফটকের কাছে ভিড় করে কৌতুহলী চোখ। বাবা বাড়িতে। তিনি শুনেছেন একটি মুত্যুর খবর। তিনি আমার কান্নার দিকে কোনও ঢিল ছোঁড়েন না। আমাকে কাঁদতে দেন। বাড়ির সবাই আমাকে প্রাণভরে কাঁদতে দেয়।
ঢাকায় ফিরে শ্মশান শ্মশান ঢাকাটি আমার আর সয় না। অসীম সাহার বাড়িতে যাই, অঞ্জনা সাহা, অসীম সাহার স্ত্রী, আমাকে আলিঙ্গন করেন শোকে। আমরা এক একটি কাঁধ খুঁজছিলাম মাথা রেখে কাঁদার। গভীর গোপন দুঃখগুলো প্রকাশের জন্য মানুষ খুঁজছিলাম আমরা। রুদ্রহীন এই নিস্তরঙ্গ নিঃসঙ্গ জগতের কথা বলতে থাকি আমরা। একসময় আমাদের শোক কোনও শব্দে প্রকাশ হয় না। আমাদের প্রতিবিন্দু অশ্রু রুদ্রর জন্য। আমাদের প্রতি কণা দীর্ঘশ্বাস রুদ্রর জন্য। কাছে পিঠে কোথাও যদি রুদ্র তুমি থাকো, দেখ, দেখ যে তোমার এই প্রস্থান আমরা কেউই গ্রহণ করতে পারি না। সম্ভব হয় না আমাদের কারওর পক্ষেই।
যে মানুষটি ধর্মে বিশ্বাস করত না, তার জানাজা হবে, কুলখানি হবে। এগুলোকেও যদি অন্তত বন্ধ করা যেত! শক্তি নেই রুদ্রকে ফিরিয়ে আনার। শক্তি নেই ধর্মকে বিদেয় করার রুদ্রর আশপাশ থেকে। আমাদের অক্ষমতা, অপারগতা নিয়ে আমরা নির্বোধের মত বসে থাকি।
শাহরিয়ার আজকের কাগজ পত্রিকার সাহিত্য পাতার সম্পাদক। আমাকে একদিন অনুরোধ করল রুদ্রকে নিয়ে কিছু লিখতে। লেখায় প্রকাশ হয় না রুদ্রর না থাকার কষ্ট। কেবল হৃদয় খুলে যদি দেখাতে পারিতাম। কাকে দেখাবো! কাউকে দেখাতে ইচ্ছে করে না। কষ্টগুলো আড়াল করে রাখি। সংগোপনে কেবল নিজের জন্য রাখি। রুদ্রই যদি নেই, দেখে আর কার কী লাভ!
ইসহাক খান নামে রুদ্রর এক বন্ধু লিখছেন বলছেন খিস্তি ছুঁড়ছেন আমার বিরুদ্ধে, আমি নাকি রুদ্রর মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমিই রুদ্রকে হত্যা করেছি। কী করে হত্যা করেছি, তা অবশ্য তিনি বলেননি। তাঁর লেখা পড়ে আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। ইসহাককে আমি চিনি দীর্ঘদিন। রুদ্রর কাছে প্রায়ই আসতেন। সংসারে অভাব ছিল তাঁর, রুদ্রর উদার হস্ত, বন্ধুকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করত। ইসহাকের সঙ্গে যতবারই দেখা হয়েছে আমার, অন্তর ঢেলে আপ্যায়ন করেছি। ইসহাক খান গল্প লেখেন, গল্পকার হিসেবে তেমন টাকা রোজগার করতে পারেননি, এখন কুৎসা রটিয়ে রোজগার করছেন। তসলিমা বিষয়ে যে কোনও লেখাই এখন পত্রিকাগুলো লুফে নেয়। কিছু ছাপাতে তাঁর এখন আর অসুবিধে হয় না। ইসহাকের লেখা পড়ে, আমি নিশ্চিত, পাঠকেরা চুক চুক করে দুঃখ করেছে রুদ্রর জন্য আর আমাকে ছিনাল পিশাচ খানকি বলে গাল দিয়েছে। রুদ্রর এক বন্ধু একদিন হেসে বলল, ‘রুদ্র না থাকায় মাগনা মদ খেতে পাচ্ছেন না বলে ইসহাকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!’ রুদ্রকে নিয়ে বাণিজ্য করার ধুম পড়েছে চারদিকে। একদিন সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল নামের এক কবি আসে, আমাকে লেখা রুদ্রর চিঠিগুলো যেন তাকে দিই, ছাপবে সে। আমি না বলে দিই। এই দুলালই রুদ্রর ট্রাক থেকে পেছনে রিক্সায় বসা আমার দিকে দলা দলা ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়েছিল।
যে কাজটি সবচেয়ে জরুরি সে কাজটি করি। রুদ্রর সমগ্রটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিই। রুদ্রর খুব ইচ্ছে ছিল তার সমগ্র প্রকাশ হোক। বেঁচে থাকলে কেউ প্রকাশ করেনি। রুদ্র কি তাই মরে গেল! মরে গিয়ে তার সমগ্র করার সুযোগ দিয়ে গেল! যা কিছু জীবনে সে লিখেছিল, সব নিয়ে সমগ্র। প্রকাশক বিদ্যাপ্রকাশ। খোকা এবার আর রুদ্রর সমগ্র বের করতে অনিচ্ছ! প্রকাশ করেননি। বইয়ের রয়্যালটি চলে যাবে রুদ্রর ভাই বোনদের কাছে। সম্পাদনার দায়িত্ব অসীম সাহার। আমার দায়িত্ব প্রুফ দেখা। ইত্যাদি প্রেসে ছাপা হতে থাকা রুদ্রর লেখাগুলোর প্রুফ যখন দেখি ঘরে বসে, যেন প্রুফ দেখি না, দেখি রুদ্রকে। যেন বসে আছে পাশে, শুনছে সে, আমি তার কবিতাগুলো পড়ছি, বার বার পড়ছি। প্রতিটি শব্দ পড়ছি, প্রতিটি অক্ষর। মেঝের ওপর একরাশ কাগজের মধ্যে সারা সারা রাত প্রুফ দেখতে দেখতে কোনও কোনও সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি ওই কাগজের ওপরই মাথা রেখে। স্বপ্নে রুদ্র আর আমি দুজন আমরা হাতে হাত রেখে হাঁটি আর কবিতার কথা বলি।
রুদ্র কমিটি গঠন করে অসীম সাহা এবং আরও কয়েকজন রুদ্রর নামে মেলার আয়োজন করেন। মেলায় বই বিক্রি হয়, কুটির শিল্পের জিনিসপত্র বিক্রি হয়। এই মেলাই অকাল প্রয়াত এক প্রতিভাবান কবিকে প্রতিবছর স্মরণ করার দায়িত্ব নিয়েছে।
রুদ্রকে নিয়ে অনুষ্ঠানে এখন অনেক বড় বড় লেখকরাই বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুদ্রকে স্মরণ করেন, যাঁরা ইচ্ছে করলেই পারতেন রুদ্রকে ঢাকায় একটি চাকরি যোগাড় করে দিতে। রুদ্র তো দ্বারে দ্বারে কম ঘোরেনি। সেই গানটি, ভাল আছি, ভাল থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো টেলিভিশনের একটি নাটকে ব্যবহার হওয়ার পর লোকের মুখে মুখে ফেরে। বেঁচে থাকলে কী বিষম আনন্দ পেত রুদ্র। বেঁচে থাকলে তার গান কি টেলিভিশনের কেউ ব্যবহার করতে চাইত! কে জানে! আকাশের ঠিকানায় আমি প্রতিদিন চিঠি লিখি রুদ্রকে। চিঠি সে পাক বা না পাক, লিখি।
১২. বৈধ অবৈধ
অবকাশ থেকে আমার সব জিনিসপত্র, আরমানিটোলা থেকে যেগুলো তুলে নেওয়া হয়েছিল, মাকে বলেছিলাম নিয়ে আসতে, বৈঠকঘরের বইয়ের আলমারিতে রাখা আমার বইগুলো তো আনবেনই, আলমারিটিও যেন আনেন। ময়মনসিংহে ট্রাক ভাড়া করে মা জিনিসপত্র ট্রাকে তুলে নিয়ে এলেন শান্তিবাগের বাড়িতে। তখন রাত অনেক হয়ে গেছে। জিনিসপত্র ঘরে ওঠানো হলে দেখি সব আছে, কেবল বইয়ের আলমারিটিই নেই। মা ক্লান্তিতে নুয়ে আছেন। ঘামছিলেন। মাকে ধমকে আরও ঘামিয়ে দিই।
‘বুকশেল্ফ আনো নাই কেন?’
মা বললেন, ‘কত চাইছি, তর বাপে দিল না। বইয়ের আলমারিটি আমার নিজের না হলেও বাপের।’ কিন্তু মেয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, দেওয়া কি যেত না আলমারিটি! মা কেঁদে ফেলেন, ‘আমি কি করতাম! তর বাপেরে এত কইলাম। তর বাপে কিছুতেই দিল না।’
আমি চেঁচিয়ে বলি, ‘দিল না কেন? বুকশেলফে তো আমার বই ই ছিল। এহন খালি বুক শেলফের মধ্যে কী ঘোড়ার ডিম সাজাইব? সব বই তো নিয়া আইছি। অবকাশে কেউ বই পড়ে? কি করব আলমারি দিয়া? খাইব?’
মা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, ‘আমি কইছি তর বাপেরে যে এইডা দেইন, মেয়েডা কইয়া দিছে, বই রাখব। ভ্যাংচাইয়া উডে। কয় এইডা আমি বানাইছি। তার দরকার লাগলে সে কিন্যা নিব নে।’
আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ‘সে দিল না তো তুমি জোর কইরা নিয়া আইলা না কেন! ট্রাকে যখন উডাইছো আমার জিনিসপত্র, কেন ওইডাও তুইল্যা লইলা না। এহন বই যে সব আনছো, বই আমি রাখবো কই? বুকশেল্ফটাই তো সবচেয়ে দরকার ছিল। কি রকম বাপ হইছে যে একটা বুকশেল্ফ দিতে পারে না নিজের মেয়েরে!’
বাবার ওপর রাগ আমার গিয়ে পড়ে মার ওপর। মা আমার গাল খেয়ে বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদেন। কারও কান্না আমার সহ্য হয় না।
দুপাশে সাইডটেবিল সহ নরম স্পঞ্জের গদিঅলা নতুন একটি বড় খাট, লেখার টেবিল, চেয়ার, কাঠের সোফা কেনার সামর্থ নেই বলে বেতের সোফা, চারটে ডিজাইন করা চেয়ার সহ খাবার টেবিল, কাপড় চোপড় রাখার কাঠের আলমারি, থালবাসন রাখার আলমারি সব ধীরে ধীরে কিনে এনে বাড়িটি সাজিয়েছি। সব করেছি একা, ভাল কিন্তু অত দামি নয় জিনিস পেতে অনেক দোকান ঘুরেছি, দোকান থেকে ঠেলাগাড়িতে মাল তোলা, ঠেলাগাড়ির সঙ্গে সঙ্গে রিক্সা নিয়ে আসা, মাল ঘরে ওঠানোর ব্যবস্থা করা, কোন জায়গায় কোনটি বসবে তা ঠিক করে দেওয়া। কেউ কোনও টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেনি। বইয়ের আলমারিটি খালি পড়ে থাকবে অবকাশে, তাই ইচ্ছে ছিল ওটি নিয়ে এসে মেঝেয় পড়ে থাকা বইগুলো রাখব। কিন্তু বাবা তা হতে দিলেন না। বাবা আমার সংসার ভাঙার বেলায় বেশ ওস্তাদ, সংসার যখন গড়ি তখন তিনি ফিরে তাকান না। ঠিক আছে, না তাকান, তাঁকে আমার জীবনের কোনও কিছুতেই কোনও প্রয়োজন নেই। আমার জীবনে তিনি তাঁর নাক যেন কখনও না গলাতে আসেন। আমার সিদ্ধান্তেই আমার জীবন চলবে, আত্মীয় স্বজন কাউকেই আমার প্রয়োজন নেই। আমাকে তাদের প্রয়োজন হতে পারে, আমার যেন কখনও কারও প্রয়োজন না হয়।
সংসার ভাবনা আমাকে ঘিরে থাকে সারাক্ষণ। মার আনা পুরোনো খাটটি পেতে দিই অন্য ঘরে, যে ঘরে আত্মীয় বা অতিথি যে কেউ এলে থাকবে। কার্পেট বিছিয়ে দিই বৈঠকঘরে। হাঁড়িপাতিল বাসন কোসন পাঠিয়ে দিই রান্নাঘরে। লিলির বড় বোন কুলসুমকে মা নিয়ে এসেছেন শান্তিবাগে। কুলসুমকে দিয়ে ঘরদোর পরিস্কার করিয়ে রান্নাঘরের জিনিসপত্র রান্নাঘরে সাজিয়ে কি করে কাটা বাছা করতে হবে, কি করে রান্না করতে হবে সব শিখিয়ে দেন। এই রান্নাঘর তো আর অবকাশের রান্নাঘরের মত নয়, এখানে বসে নয়, দাঁড়িয়ে রান্না করতে হয়, গ্যাসের চুলো, মাটির চুলো নয়। এখানে কোনও উঠোন নেই যে হাঁস মুরগি কাক পাখিদের জন্য নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাত তরকারি ছুঁড়ে ফেলা যাবে, থাল বাসন ধুয়ে পানি ছুঁড়ে দেওয়া যাবে কোনও গাছের শিকড়ে। এখানে প্লাস্টিকের ব্যাগে বা বালতিতে ময়লা জমিয়ে রেখে বাইরের আবর্জনা ফেলার স্তূপে ফেলে দিয়ে আসতে হয়। বাড়িটি আমি মনের মত করে সাজাতে ব্যস্ত, রান্নাঘরের দিকে যাবার আমার সময় নেই, ও নিয়ে আছেন মা আর কুলসুম। আমাকে খুব যত্ন করে খাবার টেবিলে খাবার দেওয়া হয়। আমি খাবার সময় মা পাশে দাঁড়িয়ে পরেবেশন করেন। আমার কখন কি লাগবে, না চাইতেই মা এগিয়ে দেন সব। মা প্রায়ই ময়মনসিংহে চলে যান, অবকাশ থেকে চাল ডাল তেল পেঁয়াজ যতটা সম্ভব সংগ্রহ করে আনেন। আমার অজান্তেই এসব করেন। কাঁচা বাজারটা আমিই করি শান্তিনগরের বাজার থেকে। বাইরের কাজগুলো করতে অনেক সময় মিলনকে নিয়ে বেরোই। মিলন তার বোনের বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়িতে উঠে এসেছে। বাবা তাঁর এক বন্ধুকে ধরে মিলনের জন্য একটি চাকরি যোগাড় করে দিয়েছেন। চাকরিটি মিলন করছে ঠিকই কিন্তু তার মন পড়ে থাকে ময়মনসিংহে। ইয়াসমিন ময়মনসিংহে বসে মাস্টার্স পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সপ্তাহের ছুটির দিনটি কবে আসবে পুরো সপ্তাহ মিলন তারই অপেক্ষা করে। বৃহস্পতিবার বিকেলে সে আর বাড়িতে ফেরে না, আপিস থেকেই সোজা চলে যায় ময়মনসিংহে। কখনও কখনও ছুটি ছাটায় ইয়াসমিন ঢাকায় এসে কাটিয়ে যায়। মার ঢাকা ময়মনসিংহ দৌড়োদৌড়ি করে কাটে। ময়মনসিংহে আমি পারতপক্ষে যাই না। আমি ব্যস্ত আমার চাকরি নিয়ে, লেখালেখি নিয়ে, আর নতুন সংসারটি নিয়ে।
একদিন একটি ফোন আসে হাসপাতালে। মিনারের ফোন। আর ঘণ্টা কয়েক পর সে চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছে আমেরিকা, আমি যেন একবার তার সঙ্গে দেখা করি। সে তার বাড়ির ঠিকানা দেয়। হাসপাতাল থেকে একটি বেবি ট্যাক্সি নিয়ে যাই তার বাড়িতে। বাড়ির সামনে বেবি ট্যাক্সিটি দাঁড় করিয়ে রেখেই মিনারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। মিনার মদ খেয়ে টাল হয়ে ছিল। গলায় অনেক গুলো চুমুর লাল দাগ। বুজে যেতে চাওয়া চোখ কোনওরকম খুলে রাখছিল। মিনারের প্রেম নিয়ে, ধনী মহিলাটির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আমি কোনওদিন কোনও প্রশ্ন করি নি, সেদিনও করি না। মিনার নিজেই বলে সেই মহিলাই তাকে আমেরিকা পাঠাচ্ছেন। মিনার রুদ্রর কথা তোলে, বলে রুদ্র যেদিন মারা গেল, সেদিন বিকেলে সে টিএসসিতে গিয়েছে যেখানে রুদ্রকে এনে রাখা হয়েছিল, রুদ্রকে স্পর্শ করে মিনার কেঁদেছে, একটি কথাই বার বার সে বলেছে, রুদ্র আমাকে ক্ষমা করে দিও। মিনারের মধ্যে যেমন একটি নিষ্ঠুর মিনার বাস করে, তেমনি একটি হৃদয়বান মিনারও হয়ত বাস করে। মিনারের কোন রূপটি সত্যিকারের রূপ কোনওদিন আমার জানা হয়নি। তাকে কোনওদিন আমার খুব আপন মানুষ বলে মনে হয়নি। ভেবেছিলাম তার সঙ্গে শেষ দেখাটি করেই চলে যাবো কিন্তু সে হঠাৎ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমাকে বিছানায় টেনে নেওয়ায় তক্ষুনি চলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বিছানায় মিনার আমাকে কেন নেয়! ধর্ষণ করতে! মিনারের শরীরের জন্য আমার শরীরে কোনওরকম আবেগ ছিল না। তার কাছে এই ব্যপারটি মজার একটি খেলার মত। জীবনের অনেক কিছুই তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ খেলা। আমার সঙ্গে মিনারের সম্পর্কটি মিনারের জন্য বা আমার জন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। তার কাছে সবচেয়ে যে জিনিসটির গুরুত্ব ছিল, সেটি বিচিন্তা। বিচিন্তা পত্রিকাটি বেশ ভাল চলছিল, কিন্তু সেটিও তার কাছে খেলা হয়ে উঠল, নদীর পাড়ের বালুতে মিছিমিছির ঘর বানানো খেলার মত, সন্ধের আগে আগে খেলাঘর পায়ে মাড়িয়ে বাড়ি চলে যাওয়ার মত করে মিনার চলে যাচ্ছে। হতে পারে বিচিন্তা ছাপতে যে মানুষটি টাকা দিচ্ছিলেন তিনি আর দেবেন না সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হতে পারে মিনারের আর ভাল লাগছিল না পত্রিকা সম্পাদনা করতে। অথবা হেথা নয় হোথা নয়, যেথায় সোনার হরিণ আছে সেথা যেতে সে ব্যাকুল হয়ে উঠছিল তাই বিচিন্তার চিন্তা বাদ দিয়ে বিচিন্তাকে মায় দেশটাকেই টা টা বাই বাই জানিয়ে দিয়েছে। আজকাল মেধাগুলো এভাবেই পাচার হয়ে যাচ্ছে। এ দেশের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পদার্থবিদ অংকবিদ সব গিয়ে বিদেশের রেস্তোরাঁয় বাসন মাজে। এতে সপ্তাহ গেলে বা মাস গেলে যে কটি ডলার হাতে আসে, তা বাংলাদেশের টাকায় বেশ বড় অংকের। বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ আলী মিনার ওরফে মিনার মাহমুদ আমেরিকায় গিয়ে বাসন না মাজলেও ট্যাক্সি ড্রাইভিং এ নিজের কেরিয়ার গড়ে তুলেছে। আমার সঙ্গে দুদিন ফোনে কথা হয়েছে। মিনারই ফোন করেছিল, কাগজের সম্পর্কটির কাগুজে মিমাংসার জন্য। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ওই একটি সম্পর্ক যে ঝুলে আছে। কাগজের সম্পর্কের মূল্য আমার কাছে নেই বলেই হয়ত মনে পড়েনি। যেরকম নিরুত্তাপ সই ছিল সম্পর্কের জন্য, সম্পর্ক ভাঙার জন্য একইরকম নিরুত্তাপ সই দিয়ে দিই। তার এক দূত এসে কাগজে সই নিয়ে যায়, সেই দূতই তাকে কাগজখানা পাঠিয়ে দেয় আমেরিকায়।
একটি জিনিস আমি লক্ষ করেছি, কারও সঙ্গে আমার সম্পর্ক একবার গড়ে উঠলে, সে যে সম্পর্কই হোক, সে সম্পর্ক অন্তত আমার দিক থেকে ভাঙে না। দীর্ঘদিন কারও ওপর আমি রাগ পুষে রাখতে পারি না। সব বরফই হৃদয়ের উত্তাপে গলে জল হয়ে যায়। কারওর ওপরই আমার ঘৃণা নেই। কেউ কোনও ভুল করলে আমি বুঝতে চেষ্টা করি কেন সে ভুলটি করেছে। নিজের ভুলগুলো নিয়েও আমার একইরকম ভাবনা। ক্ষতি করার উদ্দেশ্য কারওর যদি থাকে, আমি নিজেকে তার থেকে দূরে সরিয়ে নিই কিন্তু সম্পর্ক বিষাক্ত হতে দিই না। আমার এই চরিত্রটি অনেকটা মার চরিত্রের মত। মা খুব দ্রুত ক্ষমা করে দিতে পারেন মানুষের যে কোনও ভুল। মার চরিত্রের এই দিকটি আমার খুব অপছন্দ, কিন্তু এই চরিত্রটিই আমি গোপনে গোপনে ধারণ করে বসে আছি। মিনার যখন আমাকে দেখা করতে ডেকেছিল, আমি জানি তার সঙ্গে আমার মনের কোনও সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে আমি কখনই বসবাস করব না, কিন্তু সে আমার বন্ধু ছিল একসময়, একসময় সে আমাকে সামান্য হলেও আনন্দ দিয়েছিল, চলে যাওয়ার দিন কেন তাকে আমি কিছু শুভেচ্ছ! দেব না! দেখেছি, কোনও শত্রুর জন্য আমি কোনও অমঙ্গল কামনা করতে পারি না। বাবা আমার সঙ্গে অতবড় শত্রুতা করার পরও বাবার কখনও কোনও রকম ক্ষতি হোক আমি তা চাই না। মাকে সারা জীবন ধরে বাবা হেলা করেছেন, কষ্ট দিয়েছেন, তারপরও মা বাবার কোনও অমঙ্গল চান না। বাবার সামান্য সর্দিজ্বরেই অস্থির হয়ে পড়েন সেবা করতে। মা ভালবাসেন বাবাকে, সেটি একটি কারণ। কিন্তু ভালবাসার সম্পর্ক না থাকলেও মার আচরণ খুব ভিন্ন নয়। গীতা আর হাসিনা মাকে মা বলে গণ্য করে না, মাকে অপমান করতে কোনও দ্বিধা নেই তাদের, তারপরও মা ওদের জন্য পারলে জীবন দেন। আবদুস সালামের বাড়িতে মার গরুটি বড় হচ্ছিল, একদিন সালাম এসে জানাল যে গরু হারিয়ে গেছে। কেন সালামদের বাড়ির কোনও গরু হারালো না, কেবল মার গরুটি হারালো, এ প্রশ্ন মার মনে উদয় হয়েছে, কিন্তু সালাম বাড়ি এলে ঠিকই মা তাকে আদর করে খেতে বসান। লিলির মাকে গালগাল করলেন আজ, কালই তাকে নিজের পরনের শাড়িটি খুলে দিয়ে দেন। লিলি বা কুলসুমের ওপর রাগ করে গালে শক্ত চড় কষালেন, ঘণ্টাখানিক পরই মার রাগ জল হয়ে যায়। হাতে টাকা থাকলে তখন দোকানে গিয়ে লিলি বা কুলসুমের জন্য কিনে আনেন ভাল কোনও জামা বা লালফিতেঅলা সেণ্ডেল। মার চরিত্রে কোনও দৃঢ়তা নেই, যেটুকু আছে সেটুকুই পলকে ভেঙে যায়। আমার দৃঢ়তাও লক্ষ করেছি খানখান হয়ে পড়ে যখন তখন। এর কারণ কি নিঃসঙ্গতা! হয়ত বা। দৃঢ়তা তাকেই মানায় যার গায়ের জোর আর টাকার জোর আছে অথবা সমাজে একটি পোক্ত অবস্থানে বাস করার জোর আছে। যে নাইম একসময় আমার অনিষ্ট করার জন্য অথবা আমার সুখে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য হেন কাজ নেই যে করেনি, আরমানিটোলার বাড়িঅলা আমাকে নোটিশ দিয়েছিল বাড়ি ছাড়ার, সে নাইমের ষড়যন্ত্রের কারণেই, এও শুনেছি যে সুগন্ধা পত্রিকাটির লেখাটির পেছনে এবং পত্রিকাটি বাবার হাতে পৌঁছোর পেছনে নাইমের বড় একটি অবদান আছে — সেই নাইমের সঙ্গেও আমার দেখা হয়, কথা হয়। হঠাৎ হঠাৎ সে শান্তিবাগের বাড়িতে আসে। নাইম আমার একলা থাকার শখের বারোটা বাজাতে চেয়েছিল। আমার শখের ওপর দশ টনের ট্রাক চলে গেছে, গুঁড়ো করে দিয়ে গেছে আমার শখের হাড়গোড়, তারপরও আমার শখ যায়নি। শখ যে আমি যে করেই হোক মেটাচ্ছি, তা সে শান্তিবাগের বাড়িতে এসে দেখে যায়। আমার সুখী য়চ্ছল জীবন দেখে আড়চোখে। নাইম হিংসেয় মরে, সে আমি অনুমান করি। আমার কলামের জন্য দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে অনুরোধ আবদার আসে, নাইম কিন্তু তার ভোরের কাগজে লেখার জন্য আমাকে কখনও বলে না। সে চায় না আমাকে আরও বিখ্যাত হতে দিতে। ভোরের কাগজে লিখছি না বলে আমার কোনও আক্ষেপ নেই, এমনিতে আমি অনেকগুলো পত্রিকায় লিখে কুলিয়ে উঠতে পারি না। নাইমের দোষে বা তার ভাগ্যের দোষে এত চালাক চতুর হয়েও তার পরিকল্পনা মত সব কিছু এগোয় না। ভোরের কাগজ থেকেও তাকে একসময় তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপরও দমে যাওয়ার পাত্র সে নয়। নতুন উদ্যমে এবার আর পত্রিকা নয়, নিউজ এজেন্সি খুলে বসেছে। খুব ধুমধাম করে নাইম একটি বিয়ে করেছে। চট্টগ্রামের মেয়ে। বিএ পাশ। দেখে শুনে বুঝে সুঝে বিয়েটি সে করেছে। পতিব্রতা স্ত্রী হওয়ার গুণ যে মেয়ের মধ্যে আছে, তেমন মেয়েকেই ঘরে এনেছে। মেয়ে রাঁধবে বাড়বে চমৎকার, শ্বশুর শাশুড়ির যত্ন নেবে, দেবর ননদের দেখভাল করবে, স্বামী যাহা বলিবে তাহাই করিবে জাতীয় মেয়ে। এমন মেয়ে বিয়ে করেও নাইম আমার বাড়িতে আসে। আমার শরীরের দিকে সে ঝুঁকে থাকে। আমি বাধা দিই না শরীরের সম্পর্কে। দীর্ঘদিনের পুরুষস্পর্শহীন শরীরটি নাইমের স্পর্শে কেমন তির তির করে কেঁপে ওঠে। দীর্ঘদিন নিজের অবদমিত ইচ্ছেগুলো মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়, দীর্ঘদিন অন্যের ইচ্ছের সঙ্গে আপোস করে করে নিজের ভেতরে একটি ইচ্ছের জন্ম হয়। ইচ্ছেটি আমার, ইচ্ছেটি অন্য কারওর নয়। ইচ্ছেটিকে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি। ইচ্ছেটির হাতে হাত রেখে বসে থাকি মুখোমুখি, নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলি, ‘এ শরীর আমার, শরীর সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্বও আমার।’ শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাবার অন্য কোনও উপায় যদি আমার জানা থাকত, তবে নাইমের সঙ্গে মাসে একবার কি দুবার যে সম্পর্কটি হয়, হত না। তার পরও হয়েছে, ইচ্ছে করেছি বলে হয়েছে। সমাজের হাজার রকম যুক্তিহীন নিয়ম অস্বীকার করার মত এই নিয়মটিও আমি অস্বীকার করি যে আমার শরীর কেউ স্পর্শ করলে আমি পচে যাব। পান থেকে চুন খসলে লোকে নষ্ট বলে, অবশ্য মেয়েদের কিছু খসলেই বলে। পুরুষেরা বলে মেয়েদের অমূল্য সম্পদের নাম সতীত্ব। পুরুষেরাই সমাজের এই নিয়মগুলো তৈরি করেছে। মেয়েদের বাধ্য করা হয় বিয়ের আগে কুমারীত্ব আর বিয়ের পর সতীত্ব রক্ষা করতে। বিয়ে নামক সামাজিক নিয়মটি মেয়েদের শরীর এবং মনকে পুরুষের সম্পত্তি করে ফেলে। এই নিয়মের জালে আটকা পড়ে আছে মেয়েরা। নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে বইটির প্রথম পাতায় একটি কথা লিখেছিলাম, শৃঙ্খল ভেঙেছি আমি, পান থেকে খসিয়েছি সংস্কারের চুন। কিন্তু সত্যিকার শৃঙ্খল ভাঙতে কি আমি পেরেছি! নাকি ভাঙার একটি গোপন ইচ্ছে নিয়েই বাস করি কেবল! শৃঙ্খল ভাঙার ইচ্ছেটি যেন কেবল বলার জন্য বলা না হয়, প্রাণপণে জীবনে তার প্রয়োগ চেয়েছিলাম। সেই কচি বয়সে আমাকে যখন বোরখা পরানোর চেষ্টা হয়েছিল, সেই যে বোরখা ছুঁড়ে ফেলেছিলাম, সংষ্কার না মানার শুরু তখনই। রিক্সার হুড মাথায় ঘোমটার মত তুলে মেয়েরা বসবে, এই নিয়ম ভেঙেও রিক্সার হুড ফেলে দিয়ে রিক্সায় চড়েছি ছোট্ট ঘিঞ্জি শহর ময়মনসিংহে। লোকে হাঁ হয়ে দেখেছে, দেখুক। মন্দ বলেছে, বলুক। আমার ইচ্ছে হয়েছে বলে করেছি, আমার ভাল লেগেছে বলে করেছি। সামাজিক নিয়মগুলোয় আমি কোনও যুক্তি পাইনি বলে করেছি। সোজা কথা। সাফ কথা। বাবা মা ছেলে পছন্দ করবেন, তারপর মেয়ের বিয়ে হবে। সেই নিয়মও মানিনি। প্রেম করতে মানা। প্রেম করেছি। স্বামী যেমনই হোক, মানিয়ে চলা নিয়ম, সেই নিয়ম মানিনি। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা, আড্ডা দেওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া মানা, সেই নিয়মও মানিনি। আমি আমার নিয়মে চলতে চাই। যে নিয়মটিকে আমি পালনযোগ্য মনে করি, সেটি গ্রহণ করতে চাই, বাকি নিয়ম যেগুলো আমারে আমিত্ব নষ্ট করে, সেগুলোকে বর্জন করতে চাই। কোনও অযৌক্তিক কিছুর সঙ্গে, কোনও মন্দের সঙ্গে মানিয়ে চলতে যে পারে পারুক, আমি পারি না। আমি না পেরে দেখিয়েছি আমি পারি না। খুব অল্পদিনেই আমি বুঝতে পারি, নাইম আমার শরীরে তার তৃষ্ণা মেটাচ্ছে, এতে তার লাভ হলেও আমার কোনও লাভ হচ্ছে না। আমি কোনও তৃপ্তি পাচ্ছি না এই সম্ভোগে। এর কারণ আমি একটিই খুঁজে পাই, নাইমের জন্য আমার কোনও ভালবাসা নেই। একসময় যখন তাকে ভাল লাগত, তখন তৃপ্তি হত। ভাললাগাটিও যখন ফুরিয়ে যায়, তখন সম্ভোগ নিতান্তই শারীরিক যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়ায়। ভালবাসা না হোক ভাল লাগা বলে কিছু থাকতে হয়, কেবল শরীরের জন্যই শরীর উত্তেজিত হয় না। ধীরে ধীরে আরও একটি ইচ্ছের জন্ম হয় আমার মধ্যে, সেটি সম্ভোগের নামে শারীরিক যন্ত্রণাটি না মানার ইচ্ছে। এটিও সিদ্ধান্ত। একটি জিনিস আমার বিশ্বাসের ভেতরে পাকাপাকি জায়গা করে নিতে চাইছে, সেটি নিজের ইচ্ছের মূল্য দেওয়া। যে কোনও ব্যপারেই। হ্যাঁ, আমার শরীর সম্পূর্ণই আমার, এর ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার আমার ছাড়া আর কারও থাকা উচিত নয়। এ শরীর নিয়ে কি করব আমি, একে পাঁকে ফেলব নাকি মাথায় তুলব, এ আমার নিজের সিদ্ধান্তেই হবে। অন্যের সিদ্ধান্তে নয়। আমি একাধিক পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেছি, একথা জেনে অনেক পুরুষই জুলজুল করে তাকায় আমার শরীরের দিকে। যেন শরীরটি খুব সুলভ কিছু, যেন হাত বাড়ালেই মেলে। যদি হাত বাড়ালে না মেলে, জুলজুল চোখগুলো ক্রমেই বিস্ফারিত হয়। অন্য কোনও মেয়েকে যত না কাদা ঘাঁটতে হয়, যত না কাঁটাতার পেরোতে হয় পথ চলতে, আমার বেশি হয়। কারণ পুরুষের দৃষ্টিগুলো সন্দিহান, জিভগুলো বেরিয়ে আসা, চোখগুলো লোলুপ, নাকগুলো শুকর শুকর। নারী হচ্ছে ভোগের সামগ্রী, এই কথাটি সকলের মস্তিস্কের কোষে গ্রথিত। একাধিক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে বলে আমি অন্যরকম জীব, আমি এই বয়সে স্বামী সন্তানহীন জীবন কাটাচ্ছি, আমার জীবনটি অস্বাভাবিক, ঠিক তাদের মা বোন খালা ফুপু বা বউদের মত আমি নই। চোখ টিপতে হাত ধরতে গায়ে ঢলতে তাই কারও কোনও শরম হয় না। তাদের আরেকটি ভাবনা কখনও হয় না যে পুরুষও ভোগের সামগ্রী হতে পারে, নারীও ভোগ করতে পারে পুরুষকে এবং এই ভাবনাটি তো একেবারেই হয় না যে আমি ইচ্ছে না করলে এক ধর্ষণ ছাড়া কারও সাধ্য নেই আমার শরীর পাওয়া।
আমার শান্তিবাগের বাড়িতে হঠাৎ একদিন শিপ্রা উদয় হয়। শিপ্রার জীবনে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। মানুর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর সে পড়াশোনায় মন দিয়েছিল। এতে কাজ হয়েছে, সে পিজিতে ভর্তি হয়েছে। এখন সে ঢাকায় পিজির হোস্টেলে থেকে এফসিপিএসএর ক্লাস করছে। মানু থেকে মন উঠেছে শিপ্রার, এ খুব ভাল সংবাদ কিন্তু সে নতুন করে প্রেমে পড়েছে। প্রেমিকের নাম হারুন। দেখতে ফর্সা, ছোট খাটো, ভাল ছাত্র গোছের চেহারা। হারুনও পিজিতেই পড়াশোনা করছে। হাঁটুর বয়সী না হলেও শিপ্রার বুকের বয়সী হবে হারুন। এই হারুনের সঙ্গে কী করে কী করে দু কথা হয় শিপ্রার। তারপরই ওকে লেজের মত করে নিয়ে আমার শান্তিবাগের বাড়িতে হাজির। সোফায় ঘন হয়ে বসে ফিসফিস করেই ছেড়ে দেয়নি, দুজনে শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। হারুনও তাকে, মানুর মত অতটা না হলেও, শিপ্রা বলে যে আনন্দ দিতে পারে। এরকম একটি চমৎকার বাড়ি পেয়ে শিপ্রা ঘন ঘন আসতে শুরু করল হারুনকে নিয়ে। মিলনও দেখে শিপ্রার কাণ্ড। সে আগেও দেখেছে তার নিজের ভাই মানুর সঙ্গে শিপ্রার মাখামাখি। মিলন আগে অনেকবার বলেছে শিপ্রাকে, মানুর কোনও প্রতিশ্রুতিতে যেন সে বিশ্বাস না করে। শিপ্রা তখন এমনই মানু -পাগল যে কারও কোনও উপদেশই তার কানে প্রবেশ করলেও অন্তরে প্রবেশ করত না। মিলনের সামনে, শিপ্রার, আমি বুঝি, হারুনের সঙ্গে সম্পর্কটি নিয়ে খানিকটা অস্বস্তি হয়। কিন্তু অচিরে সে অস্বস্তি ধুলো ধুলো ঝেড়ে ফেলার মত ঝেড়ে ফেলে। আমি বা মিলন দুজনের কেউই শিপ্রাকে অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিই না। পুরোনো কথা শিপ্রাও আর মনে করতে চায় না। নতুন জীবন নিয়ে সে ব্যস্ত। একদিন হারুনের হাঁড়ির খবর নিয়ে পড়ল। হারুন কেন বলেছে যে তার সঙ্গে তার বউএর সম্পর্ক ভাল নয়, কিন্তু সে যে দেখলো দুজনকে সেদিন পার্কে বেড়াতে! হারুন হোস্টেল ছেড়ে শিপ্রাকে লুকিয়ে প্রায় রাতেই শ্বশুর বাড়ি চলে যায় রাত কাটাতে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় শিপ্রা রাতের ঘুম ছেড়ে দিল। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ব্যস্ত হারুনের গতিবিধি নিয়ে। কেন যায় সে এত ঘন ঘন বউএর কাছে, তবে কি তার বউকে সে ভালবাসে, কিন্তু হারুন তো শিপ্রার গা ছুঁয়ে বলেছে, তার বউএর সঙ্গে বছর দুই ধরে কোনও রকম সম্পর্ক নেই, মনের এবং শরীরের সম্পর্ক যদি থাকে কারও সঙ্গে, তবে তা শিপ্রার সঙ্গেই! বউ থাকে বউএর বাপের বাড়ি। বাচ্চাটিকে নাকি হারুন মাঝে মাঝে দেখতে যায়। কিন্তু শিপ্রার মনে সন্দেহ, কেবল বাচ্চার উদ্দেশেই যাওয়া নয়। উদ্দেশ্য বউএর সঙ্গে শোয়া। আবার শিপ্রার চোখে জল। আবার উদ্বিগ্ন সে! আবারও দুশ্চিন্তার একশ পোকা তার মাথায় কালো উকুনের মত কিলবিল করে। এই হারুনের সঙ্গেও, আমার আশঙ্কা, সম্পর্ক ঘুচবে শিপ্রার। প্রেম করবে বিয়ে হওয়া বাচ্চা কাচ্চা হওয়া পুরুষের সঙ্গে, যেখানে অবিবাহিতরাই বিশ্বস্ত হয় না, সেখানে আবার বিবাহিতকে বিশ্বস্ত করতে চাইছে সে, তাও আবার জোর জবরদস্তি করে!
‘হুমায়ুন কোথায়?’
‘ওর কথা বোলো না। ওর নাম শুনলে আমার গা ঘিনঘিন করে।’
হুমায়ুন থাকে রাজশাহী। আনন্দ হুমায়ুনের কাছে। শিপ্রার মাও চলে গেছেন রাজশাহী। খুব সংক্ষেপে তথ্যগুলো জানিয়ে শিপ্রা আবার হারুনের কথায় ফিরে এল। হারুন কি তাকে ভালবাসে না?
আমি কি করে জানব হারুন শিপ্রাকে ভালবাসে কী না! আমার নিরুত্তর মুখখানার দিকে চেয়ে শিপ্রা হঠাৎ হু হু করে কাঁদতে শুরু করে।
‘কী করব বলো তো! হারুন কি আমাকে মিথ্যে কথা বলছে যে আমাকে সে ভালবাসে!’ ‘হারুন তোমাকে ভালবাসে কি না সে তুমি বুঝবে, আমি বুঝবো কী করে!’
‘আমি তো ভেবেছিলাম ভালই বাসে, কিন্তু মনে হচ্ছে ও আমাকে মিথ্যে বলেছে।’
‘মিথ্যে যদি বলে, তবে তুমি আর লেগে আছো কেন?’
‘লেগে না থেকে যে পারি না। অনেকবার ভেবেছি ওকে ভুলে যাবো। কিন্তু ভুলতে যে পারি না।’
‘চেষ্টা করেছো?’
‘তা করেছি। লেখাপড়ায় মন দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বই খুলে কেবল বসেই থাকি, মন থাকে হারুনে।’
‘বিবাহিত লোকদের নিয়ে ঝামেলা। প্রেম করলে অবিবাহিহতদের সঙ্গে কোরো।’
‘আমাদের বয়সী বা কাছাকাছি বয়সী কোন ছেলেটা আছে এখনও অবিবাহিত?’
‘ছেড়ে দাও তো। হারুন কি করল কোথায় গেল, কি বলল, মিথ্যে বলল কী সত্যি বলল, এসব নিয়ে ভাবো কেন?’
‘ভাববো না?’
‘না।’
‘তাহলে কি কেবল শরীর?’
‘সেটিই তো তোমার প্রয়োজন। ঠিক না?’
‘কিন্তু ভালবাসাহীন কোনও স্পর্শ যে আমার শরীরকে কোনও উত্তাপ দেয় না।’
শিপ্রার চোখে চোখ রেখে আমি গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, ‘হারুনকে কি তুমি ভালবাসো?’
শিপ্রা মাথা নাড়ে। সত্যি সত্যি সে বাসে। না বাসলে হারুন তার বউএর কাছে গেলে তার কষ্ট হয় কেন!
শিপ্রার জন্য আমার মায়া হতে থাকে। আমি তাকে কোনওরকম সান্ত্বনা দিতে পারি না। ভালবাসা ছাড়া শিপ্রাও কোনও শরীরের সম্পর্কে উৎসাহ পায় না। ভালবাসার জন্য যোগ্য কোনও মানুষ আমাদের নেই। আমরা ভালবাসা পেতে চাই, দিতে চাই। কিন্তু বারবারই পুরুষের প্রতারণার শিকার হই। তারপরও ভালবাসার শখ যায় না আমাদের। এত আঘাত পাওয়ার পরও হৃদয়ের দুয়ার খুলে বসে থাকি। ভালবাসা জিনিসটি একরকম ফাঁদ, ভাল লাগিয়ে, ভালবাসিয়ে, প্রেমে পড়িয়ে পুরুষেরা অন্যরকম এক দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধে মেয়েদের। কোনও পুরুষের সঙ্গে আমার এখন ভালবাসার সম্পর্ক নেই, আমি হয়ত ততটা অনুভব করি না, কিন্তু এটি আমাকে একধরনের মুক্তি দেয়। প্রেমহীন জীবন বর্ণাঢ্য না হলেও স্বস্তিকর। আমার এখন স্বস্তিই দরকার।
এরপর একদিন খুব খুশি খুশি মুখে আমার বাড়িতে এল শিপ্রা। আমাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত আনন্দে সে জানাল যে জীবনে প্রথম সে অরগাজমের স্বাদ পেয়েছে। হারুনের সঙ্গে কবে কোথায় তার মিলন হয়েছে জিজ্ঞেস করলে সে মাথা নাড়ে। হারুন তাকে দেয়নি এটি। তবে দিয়েছে কে, অন্য আবার কার সঙ্গে তার প্রেম হল! না কারও সঙ্গে নয়। কেউ তাকে এই শীর্ষসুখ দেয়নি। সে নিজেই দিয়েছে নিজেকে। কি করে? এক মধ্য রাতে শিপ্রার শরীর জেগে উঠেছে, সে এপাশ ওপাশ করছে, তারপর নিজেই সে ঘটনাটি ঘটায়। শিপ্রা নিখূঁত বর্ণনা করে কি করে সে নিজের উত্তপ্ত শরীর শীতল করার জন্য হস্তমৈথুন করেছে। হস্তমৈথুন পুরুষের ব্যপার, সে আমি জানতাম। শিপ্রাও তাই জানত, কিন্তু নিজে সে নিজের শরীরে কোনও রকম অভিজ্ঞতা ছাড়াই যে কাজটি করেছে, তা তাকে একটি নতুন স্বাদ দিল, অরগাজমের স্বাদ। প্রথম স্বাদ।
শিপ্রার উদঘাটন করা স্বমৈথুন আমাকে আকর্ষণ করে না। শিপ্রার মত কারও প্রেমেও আমি পড়ি না। যৌনতা শিকেয় তোলা। ডাক্তারি চাকরির বাইরে যে অবসরটুকু জোটে সেটুকু আমি সাহিত্য জগতে খরচ করি।
১৩. ঘটনার ঘনঘটা
এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। বিশেষ করে দেশের রাজনীতিতে। দেশজড়ে বিশাল স্বতস্ফূর্ত স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন রাষ্ট্রপ্রধান এরশাদকে বাধ্য করেছে গদি থেকে নেমে যেতে। এরশাদের ধারণা ছিল না এই আন্দোলন এমন প্রবল হয়ে তাঁকে গদিচ্যূত করতে এভাবে ধাবিত হবে। তিনি বেশ ছিলেন। ভেবেছিলেন যে কোনও আন্দোলন তিনি অস্ত্র আর ধর্মের আঘাতে চূর্ণ করে দেবেন। জনগণ কি চায় না চায় তার তোয়াককা না করে তিনি যা চান তাই তিনি নিজেকে দিয়ে যাচ্ছিলেন। আটরশির পীরের কাছ থেকে দেশ কি করে চালাতে হবে কদিন পর পরই তার উপদেশ নিয়ে আসতেন। রাজনীতিবিদদের এরকম একএকজন পীর থাকে। দেশের রাজা মন্ত্রীদের দয়া দাক্ষিণ্যে পীরদের অবস্থা পোয়াবারো। পীরের কাছে তদবির করে চাকরি পাওয়া যায়, মন্ত্রীত্ব মেলে। হাফেজ্জী হুজুর নামের এক পীর সবাইকে চমকে দিয়ে পীরালি ব্যবসা বাদ দিয়ে রাজনীতি ব্যবসায় ঢুকেছিল। বুক ফুলিয়ে ছিয়াশি সালে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল। পীরদের রাজনীতির শখ প্রচণ্ড। আটরশির পীর, শর্ষিনার পীর এরকম হরেক রকম পীর রাজনীতির হরেক রকম ব্যবসা নিয়ে জমকালো জীবন যাপন করছেন। ঢাকায় এখন সাইদাবাদি পীরের রমরমা ব্যবসা। এই লোকটি গুলিস্তানের মোড়ে দাঁড়িয়ে একসময় পুরোনো কাপড় বিক্রি করত, আর এখন ঢাকায় বিশাল এক প্রাসাদের মত বাড়িতে বসে পীর ব্যবসা করছে। এই পীর, লোকে বলে কাঁচা ডিম হাতে নিয়েই পাকা করে ফেলে। বাচ্চা দরকার, চাকরি দরকার, কাউকে সর্বস্বান্ত করা দরকার সব দরকারের জন্য পীরের কাছে ডিম নিয়ে হাজির হচ্ছে হাজার হাজার লোক। পীরের যাদু যখন বড় এক আলোচনার বিষয়, তখন স্বয়ং এরশাদও এক যাদু দেখালেন। এরশাদের বাচ্চা কাচ্চা নেই বলে কুসংস্কারাচ্ছত মানুষ তাঁকে আঁটকূড়ে বলে ডাকা শুরু করেছে, যে পুরুষ বাচ্চা হওয়াতে পারে না সে আবার কেমন পুরুষ, এমন পুরুষ দেশ চালালে দেশের ফলন যাবে কমে ইত্যাদি কথা বাতাসে ভাসে, বাতাসকে বাগে আনতে তিনি একটি আধখেঁচড়া নাটক করলেন। অনেকটা কাঁচা ডিম পাকা করে ফেলার মত। হঠাৎ একদিন স্ত্রী রওশনকে জনসমক্ষে এনে কোলে একটি বাচ্চা বসিয়ে বলে দিলেন, এই তো তিনি বাপ হয়েছেন। এতে অবশ্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলন মোটেও থেমে যায়নি। আন্দোলন যখন তুঙ্গে, এরশাদ পুলিশকে আদেশ করেছেন মিছিলে মিটিংএ গুলি চালাতে। অজস্র গুলি চলেছে। অগুনতি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সব মৃত্যুই শোকের, সব মৃত্যুই মানুষের ভেতর ক্রোধ সৃষ্টি করেছে। যদিও অনেক মৃত্যুতে কোনও সাড়া পড়ে না, নূর হোসেনের মৃত্যু আন্দোলনকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। আশ্চর্য এক সাহসী যুবক নূর হোসেন। নূর হোসেন মিছিলে সবার সামনে ছিল। সাধারণ মানুষ। বেবি ট্যাক্সি চালাত। কোনও রাজনীতি করেনি কোনওদিন, লেখাপড়া শেখেনি খুব, বুকে লিখেছে গণতন্ত্র মুক্তি পাক, পিঠে লিখেছে স্বৈরাচার নিপাত যাক। পুলিশের গুলি গণতন্ত্র মুক্তি পাক ভেদ করে চলে গেছে। নূর হোসেন মারা গেল মিছিলে। শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু নূর হোসেনের দেখা হয়নি সে মুক্তি। গণতন্ত্রকে মুক্তি পেতে কিছুতেই দিতে চাইছিলেন না এরশাদ। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ তিনটি বছর জোট বেঁধে আন্দোলনের পর, নব্বইএর তুমুল জোয়ারে ভেসে গেল এরশাদের গদি।
এরশাদের পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে নির্বাচন হল। নির্বাচনে দুটো বড় দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। আওয়ামী লীগ আর বিএনপি। শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা একদিকে, আরেকদিকে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অষ্টম শ্রেণী পাশ সুন্দরী পুতুল ওরফে বেগম খালেদা। হাসিনা আর খালেদা যদিও এরশাদকে গদিচ্যূত করার সময় হাতে হাত রেখেছিলেন কিন্তু এরশাদ যেই না সরে গেল, যেই না নির্বাচনী প্রচারে নেমে গেলেন দুজন, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেলে দুই দলে। হাসিনা কেঁদে কেটে বুক ভাসান তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের কি করে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে খুন করা হয়েছিল সেসব কথা বলে বলে। আওয়ামী শাসনামলের ভয়াবহ দুঃশাসনের কথা বর্ণনা করেন খালেদা। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের দেশে ধর্মও হয়ে উঠল অস্ত্র। খালেদা জিয়া যদি দুকথা ধর্মের বলেন, হাসিনা চারকথা বলেন। আওয়ামি লীগ ধর্মের পরোয়া করে না, এরকম একটি দুর্নাম ছিল আগে, যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের রাষ্ট্রগঠনের চার নীতির এক নীতি। এই দুর্নাম থেকে যতই হাসিনা মুক্তি পেতে চান, খালেদা ততই কায়দা করে এটিকে ব্যবহার করেন। আশা ছিল শেখ হাসিনার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। কিন্তু ঘটনা তা ঘটে না। অনেক মানুষই বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর আওয়ামি লীগ সরকারের অরাজকতার কথা স্মরণ করে ভোট আর যাকে দিক আওয়ামি লীগের কাউকে দেয় না। ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল একদা আওয়ামি লীগের, এটি খালেদার আরেকটি অস্ত্র। নির্বাচনে দুটি জিনিসই কাজ করেছে, এক, আওয়ামি লীগ জিতে গেলে দেশে ধর্ম বলতে কিছু থাকবে না, দুই হাসিনা ভারতের কাছে বিক্রি করে দেবে এই দেশ। দুটো টোপই পাবলিক গিলেছে। অথবা দুটো দুর্নামেরই সঠিক ব্যবহার হয়েছে। আওয়ামি লীগ ভোট পায়, কিন্তু অধিকাংশের নয়। জনগণকে আওয়ামি আতংকে ভুগিয়ে খালেদা জিয়া ভোটে জিতে পেয়ারের কিছু রাজাকারদের মন্ত্রী বানিয়ে প্রধান মন্ত্রী হন। আবদুর রহমান বিশ্বাস নামের এক রাজাকারকে প্রেসিডেন্ট পদে বহাল করেন। মহা সমারোহে জামাতে ইসলামি আঠারোটি আসন নিয়ে সংসদে ঢুকেছে। ভারতের কাছে দেশ বিক্রির দুর্নাম ঘোচাতে শেখ হাসিনা মুখে ভারতবিরোধী কথা বলা শুরু করলেন। ধর্ম যাবে, এই দুর্নাম ঘোচাতেও ধার্মিক হয়ে গেলেন রাতারাতি। বিশাল করে ইফতার পার্টির আয়োজন করেন, টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমায় গিয়ে দু হাত তুলে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেন। মককা গিয়ে হজ্ব করে এলেন।। এই প্রথম দেশের প্রধান মন্ত্রী একজন মহিলা, প্রতিপক্ষ দলের পুরোধাও একজন মহিলা এ কারণে একটি আনন্দ ছিল আমার, সেই আনন্দটির শরীরে উঠে আসতে থাকে একটি অজগর, গা শিউরে ওঠা আতঙ্ক।
খালেদা জিয়া ক্ষমতায় বসার পর এরশাদকে অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু একই স্বৈরাচারি আচরণ খালেদার সরকারও দেখাতে শুরু করেছে। প্রচার মাধ্যমকে নিরপেক্ষ রাখার কথা ছিল, কথা আরও কত কিছু ছিল, কোনও কথাই ক্ষমতা পেয়ে গেলে আর কারও রাখতে ইচ্ছে করে না। সংবিধানের রাষ্ট্রধর্মটিকে সরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা বহাল করার কথাও উচ্চারণ করে না কেউ। দেশের মানুষের ভালর জন্য এ দেশের রাজনীতি নয়, রাজনীতি ক্ষমতার রাজনীতি। ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা পাওয়ার উদ্দেশ্যই সব রাজনৈতিক দলের। ক্ষমতার আনন্দ ভোগ করার উদ্দেশ্যই রাজনীতিকদের মূল উদ্দেশ্য। দেশের এহেন রাজনীতি আমাকে দুশ্চিন্তার পাঁকে ডুবিয়ে রাখে।
গাইনি বিভাগে গাধার মত পরিশ্রম করে লেখালেখির জন্য কোনও সময় পাওয়া যায় না, সে কারণে গাইনি থেকে অ্যানেসথিসিয়া বিভাগে চলে গিয়েছি। গাইনির পরিবেশও আগের মত নেই আর। নতুন ইন্টার্নি এসে গেছে, পুরোনোরা বিদেয় নিয়েছে। অধ্যাপক বায়েস ভুঁইয়াও বদলি হয়ে অন্য হাসপাতালে চলে গেছেন। আমার ইউনিটে নতুন সি এ এসেছে। তার ওপর রাত দিন ডিউটি, লেখার জন্য তেমন সময় পাওয়া যায় না। আগের চেয়ে লেখার চাপ অনেক বেড়েছে। কিন্তু লিখতে হলে তো সময় চাই। সময় কোথায়! অ্যানেসথেসিয়া বিভাগেও যে একেবারে কাজের অভাব নেই, তা নয়, রাতে যে ডিউটি নেই, তা নয়। সবই আছে। কিন্তু এখানে দু হাত হলেই চলে, দশ হাতের দুর্গা দেবী না হলেও কাজ হয়। গাইনিতে দশ হাতে কাজ না করলে কাজকে কাজ বলে গণ্য করা হয় না। আমার বাড়তি আটটি হাত নেই, যার থাকে থাকুক। আর যেহেতু পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পথ শেষ পর্যন্ত মাড়াচ্ছি না, কী দরকার অত ডুবে থেকে! তা ছাড়া যা শেখার ছিল, শেখা হয়ে গেছে। এ বিদ্যে নিয়ে দিব্যি বাকি জীবন গাইনির ডাক্তার হিসেবে কাজ করা যাবে। অ্যানেসথেসিয়া বিভাগে গাইনি বিভাগের মত চব্বিশ ঘন্টা খাটাখাটনি নেই। ছিমছাম, পরিচ্ছত, কাজের ফাঁকে চা সিঙ্গারা, ডাক্তারি আড্ডা। বিভাগের অধ্যাপক মজিবর রহমান এবং মানস পাল দুজনই চমৎকার মানুষ। বন্ধুর মত। বাকি দুজন ডাক্তার শামিমা বেগম আর দেবব্রত বণিকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রথম দিন থেকেই মধুর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শামিমার সঙ্গে। প্রথম দিনই দুএকবার দেখে শিখে গেলাম কী করে অ্যানেসিথিসিয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় দিন থেকে নিজেই দিতে শুরু করি। মাঝে মাঝে এখানেও ব্যস্ততার শেষ নেই বিশেষ করে গাইনির অপারেশন থিয়েটারে যখন দৌড়োতে হয়। এমনও হয়, সারা রাতে দুমিনিটের জন্য অবসর জোটে না, সারারাতই একটির পর একটির অপারেশন হচ্ছে। আমি এবার আর ছুরি কাঁচি হাতে নিয়ে দাঁড়াই না, আমার হাতে অজ্ঞান করার ওষুধ, অক্সিজেন, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস নেওয়ার যন্ত্রপাতি। রোগীকে ঘুম পাড়ানো, অপারেশন শেষ হয়ে গেলে রোগীর ঘুম ভাঙানো খুব সহজ মনে হলেও সহজ নয়। ঘুমের ওষুধ আর মাংসপেশি অবশ হওয়ার ওষুধ দেওয়ার পর যদি কৃত্রিম শ্বাস চালু না করা হয়, তবে শ্বাসই নেবে না রোগী। ফুসফুস থেমে থাকার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, সময় পার হয়ে গেলে রোগীর পক্ষে শ্বাস নেওয়া আর সম্ভব নয়। ঘুম পাড়াচ্ছি, অপারেশন শেষ হবে, রোগীকে টেবিলেই ওষুধ দিয়ে জাগিয়ে পোস্ট অপারেটিভ রুমে পাঠাতে হবে, সেখানেও খবর নিতে হবে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস, রক্তচাপ ইত্যাদি সব ঠিক আছে কি না। কখনও আমার হাতে কোনও রোগীর কোনও অসুবিধে হয়নি। আমার সব রোগীই সুন্দর ঘুমিয়ে যায়, সুন্দর জেগে ওঠে। একবারই হয় অসুবিধে। সেটি অবশ্য আমার কারণে নয়। সেটি উঁচু নাক মালিহার কারণে। তিনি রোগীর সিজারিয়ান অপারেশন করার জন্য তৈরি। রোগীকে অজ্ঞান করার ইনজেকশান দিয়ে রোগীর শ্বাসনালী খুঁজছি নল ঢোকাতে, দুবার চেষ্টা করে পাইনি, তৃতীয়বার চেষ্টা করতে যাবো, তখন মালিহা তার হাতের ছুরি কাঁচি ফেলে গ্লবস খুলে আমার হাত থেকে নল কেড়ে নিয়ে আমাকে কনুইয়ের গুঁতোয় সরিয়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে গেলেন আমার জায়গায়। এফসিপিএস ফার্স্ট পার্ট পাশ করার দেমাগে তিনি নল ঢোকাবেন, যেন আমার হাত থেকে এ কাজে তাঁর হাত বেশি পাকা। খুঁজে তো তিনি পেলেনই না শ্বাসনালীর মুখ, মাঝখান থেকে রোগীর সর্বনাশ করলেন। ডাক্তার দেবব্রত বণিককে ডেকে আনতে লোক পাঠালেন তিনি। বণিক এফ সিপিএস পুরোটা না করলেও অর্ধেক করেছে, ডাকা হলে সে দৌড়ে এসে সমস্যার সমাধান করে, তার পক্ষেও সহজ ছিল না শ্বাসনালী পাওয়া, আট নবার চেষ্টা করার পর অবশেষে ঢোকে নল। বণিকেরও ঘাম বেরিয়ে গেছে ঢোকাতে। অপারেশন হল। বণিকের হাতে রোগী। সুতরাং অপারেশন থিয়েটারে উঁচু নাকটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না। আমি বেরিয়ে যাই। পরদিন বণিক আমাকে জানাল যে রাগীকে সে জাগাতে পারেনি। অল্প বয়সের মেয়েটি প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়ে আর জাগেনি। আমার খুব কষ্ট হয় শুনে। বণিক রোগীকে পাঠিয়ে দিয়েছিল পিজিতে। সেখানেও চেষ্টা করে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। সবকিছুর দোষ আমার ঘাড়ে পড়ে। মালিহাই দোষটি দেন। নিজের মাতব্বরির গল্পটি তিনি কায়দা করে লুকিয়ে ফেলেন। আমি যখন কারণ দেখাই মালিহার মাতব্বরির, দেবব্রত উল্টো আমাকে দায়ী করে বলে, ‘আপনি কেন আপনার রোগী ওকে ধরতে দিয়েছিলেন?’
‘আমাকে তো ধাককা দিয়ে সরিয়ে দিল!’
‘সরিয়ে দিলে আপনি সরবেন কেন! আপনার দায়িত্ব রোগীকে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া। মালিহার দায়িত্ব অপারেশন করা।’
‘সে তো ট্রাকিয়া খুঁজতে চাইল, আমার হাত থেকে টিউব নিয়ে গেল। সে বলল ইনটিউবেশন সে করবে।’
‘আপনি দেবেন কেন? সে কী জানে এনডোট্রাকিয়াল ইনটিউবেশনের? তার কোনও অভিজ্ঞতা আছে? ওই রোগির ট্রাকিয়া পাওয়া খুব কঠিন ছিল। যখন আপনি ট্রাকিয়া পেলেন না, সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন চালিয়ে দিয়ে আমাকে খবর পাঠাতেন!’
‘অক্সিজেন দেব কী করে, আমাকে তো কাছেই যেতে দেয়নি।’
‘আপনি ওকে ধাককা দিয়ে সরিয়ে দিলেন না কেন!’
তা ঠিক, আমি কেন মালিহাকে ধাককা না দিলেও ধমকে সরিয়ে দিই নি! কয়েক রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। মেয়েটির পান পাতার মত মুখটি, সুন্দর কাজলকালো চোখদুটো সারাক্ষণই মনে পড়েছে। আসলে আমি ধাককা দিতে পারি না। উচিত কথা বলতে, উচিত কাজ করতে আমার কেন এতে দ্বিধা থাকে, কেন এত লজ্জা আমার, কেন আমি মুখ বুজে থাকি মানুষ যখন চোখের সামনে অন্যায় করে! নিজের ওপর রাগ হয় আমার। নিজের এই মাথা নুয়ে লজ্জাবতী লতার মত পড়ে থাকার দিকে আমার রাগ হয় বড়। অনেক কিছুই আমার দ্বারা হয়ে ওঠে না, আমি লক্ষ করেছি। বাড়িতে কিছু অনাকাঙ্খিত অতিথি এসে এমন দীর্ঘ দীর্ঘ ক্ষণ বসে থাকে যে আমি এখন ব্যস্ত, এখন তোমাকে বা আপনাকে সময় দিতে পারব না বলা হয় না। ভেতরে ভেতরে গুমড়ে মরতে থাকি, কেবল না কথাটিই বেরোতে চায় না মুখ থেকে। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, আমার এই না বলতে পারার অক্ষমতা। কেউ আমার বুকের দিকে হাত বাড়াচ্ছে যেন দেখিনি সে যে চাইছে, আসলে কিন্তু দেখেছি, সেই বাড়ানো হাতে দ্রুত একটি কলম বা খাতা গুঁজে দিয়ে সরল হেসে বলি, ও এটি চাইছিলে বুঝি! সেই বাড়ানো হাতে কলম বা খাতাটি নিয়ে থতমত ভাবটি যেন সে আড়াল করতে যেন বাধ্য হয়, আড়াল করতে চেয়ে যেন বলতে বাধ্য হয় যে হ্যাঁ এটিই চেয়েছিলাম। দ্রুত কিছু একটা কাজের কথা বলে হাতের নাগাল থেকে দূরে সরে যাই। অথবা সম্পূর্ণ একটি অন্য প্রসঙ্গ টানি, যে প্রসঙ্গে তার মন উদাস হয়, যেমন তোমার বা আপনার বোনের যে বিয়ে হয়েছে, স্বামীর সঙ্গে নাকি বনছে না! গালে চড়, জুতো মারা এসব তো অনেক সাহসের ব্যপার, সামান্য যে মুখের কথা, ছি ছি তোমার মনে এই ছিল! অথবা সরে যা এখান থেকে হারামজাদা, কী অসভ্যরে কী অসভ্যতাও কখনও হাজার চেয়েও বলতে পারি না। বলি না, কারণ বলতে পারি না। তাকে বুঝতে দিই না যে তার অপকর্মের ইচ্ছেটি আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি জেনে যদি সে লজ্জা পায় অথবা আশকারা পায়। তাকে আমি লজ্জা বা আশকারা পেতে দিই না। তার অসুস্থতাকে আমাকে না বোঝা শিশুসুলভ সারল্য দিয়ে সুস্থ করে তুলতে চাই। সব লজ্জা একা ধারণ করি। পুরুষের জগতে এভাবেই আমাকে গা বাঁচিয়ে চলতে হয়, বুঝতে না দিয়ে তাদের চোখ টেপা, তাদের গা ঘেসা, তাদের হাত ছোঁয়া, রসের আলাপের ফাঁক ফোঁকর খোঁজা। যেন কিছুই ঘটেনি, যেন আমি তাকে যেরকম ভাল মানুষ ভাবি, সেরকম ভাল মানুষই সে, কখনও সে কোনও অশোভন ইঙ্গিত করে না, কখনও সে সুযোগ নিতে চায় না।
এফসিপিএস না করলে সম্ভবত এই হয়, দূর দূর করে তাড়ায় নাক উঁচু ডাক্তারগুলো। আমার হাত ভাল, অপারেশন ভাল করছি, বা অ্যানেসথেসিয়া ভাল দিচ্ছি এগুলো কেউ গণনায় নেবে না। আমি ভুল করলে লোকে বলবে ওর লেখাপড়া বেশি নেই বলে ভুল করেছে, জানে না বলে ভুল করেছে। আর এফসিপিএস ডাক্তার যদি ভূল করে তবে দোষ দেওয়া হয় অন্য কিছুকে। লিভার কাটতে গিয়ে কিডনি কেটে ফেললে দোষ হয় ছুরির, ডাক্তারের নয়। ছুরিটি নিশ্চয়ই বাঁকা ছিল। হাসপাতালে সবসময়ই এফসিপিএসগুলোর সামনে মাথা নুয়ে থাকতে হয়, তারা হাঁটলে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়। তারা যখন ডাক্তারি বিষয়ে কোনও বিদ্যা ঝাড়ে, নিশ্চুপ শুনতে হয়, তারা যখন পাগালামো করে, তখন পাগলামোকে জিনিয়াসরা ওরকম একটু আধটু করেই বলেই ভাবতে হয়। বাবাকেও আমি দেখেছি, বাড়িতে অত্যাচারি রাজার ভূমিকায়, আর মেডিকেল কলেজে একেবারে নিরীহ প্রজা। কাঁচুমাচু হয়ে হাত কচলে কচলে এফসিপিএস বা এফআরসিএস পাশ করা অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলতেন। ওঁদের দেখলেই একটি সশ্রদ্ধ হাসি ফুটতো বাবার মুখে। বাবার লজ্জা ছিল, যত না গরিব কৃষকের পুত্র হওয়ার লজ্জা, তার চেয়ে বেশি এফসিপিএস না করার লজ্জা। এটি না করলেও জুরিস প্রুডেন্সের বাড়তি কিছু পড়াশোনা করে একটি ডিপ্লোমা নিয়েছেন। মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেন সংসার সামলানোর কারণেই তাঁর এফসিপিএস করা হয়নি। তা ঠিক, বাবা চাইলে এই ডিগ্রিটি নিতে পারতেন। আমি না হয় যেমন তেমন ছাত্রী ছিলাম, বাবা ছিলেন মেডিকেল ইশকুলের ভাল ছাত্রদের মধ্যে এক নম্বর। বাবার চেয়ে খারাপ ছাত্ররা বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে বাবার সামনে বুক ফুলিয়ে হাঁটেন। বাবার নিজের অনেক ছাত্রই বাবার চেয়ে অনেক বড় হয়ে বসে আছে। আমিও কি বাবার মত হচ্ছি! আমিও তো বাবার মত নিজের অস্তিত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে বড় অস্বস্তিতে ভুগি। বড় ডাক্তারদের সামনে বাবাকে কাঁচুমাচু হতে দেখলে আমার কখনই ভাল লাগত না। একবার বাবাকে অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না এমন এক ডাক্তারের সামনে মাথা উঁচু করিয়েছি। প্রেসিডেন্ট কবি এরশাদ এশীয় কবিতা উৎসবের আয়োজন করছেন, তিনি আমাকে খুঁজছেন আমন্ত্রণ জানাতে, এরশাদের খোঁজার কারণে স্বাস্থ্য সচিব, তিনিও কবি, আমার খোঁজ করতে লাগলেন। আমি ময়মনসিংহ মেডিকেলের ছাত্রী ছিলাম এটুকুই বোধহয় তাঁর জানার দৌড়, তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজেন অধ্যক্ষ মোফাখখারুল ইসলামের কাছে ফোন করে তাঁকে দায়িত্ব দিলেন আমাকে খুব জরুরি ভিত্তিতে প্রেসিডেণ্টের আমন্ত্রণ পৌঁছে দিতে। স্বাস্থ্য মন্ত্রী আর স্বাস্থ্য সচিবের সরাসরি আদেশ বা অনুরোধ পাওয়া কোনও এক মেডিকেল কলেজের কোনও এক অধ্যক্ষ মোফাখখারুল ইসলামের জন্য অকল্পনীয় ব্যপার। আমার খোঁজ পাওয়ার জন্য মোফাখখারুল ইসলাম বড় বিগলিত হাসি নিয়ে একাধিকবার বাবার দ্বারস্থ হলেন। বাবা নিশ্চয়ই তখন কাঁচুমাচু মোফাখখারুলের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি দৃশ্যটি কল্পনা করে স্বস্তি পাই। বাবা আমাকে ঢাকায় ফোন করে বড় সুখী সুখী কণ্ঠে আমাকে খবরটি জানিয়েছিলেন। যদিও এরশাদের আমন্ত্রণে এশীয় কবিতা উৎসবে আমি অংশ নেব না, এশীয় কবিতা উৎসবের প্রতিবাদে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কবিদের নিয়ে যে জাতীয় কবিতা উৎসব হয়, আমি শুরু থেকেই সেখানে, তারপরও আমার অন্যরকম আনন্দ দেয় এরশাদের এই আমন্ত্রণটি। আনন্দ দেয় এই জন্য যে এই আমন্ত্রণের কারণে স্বাস্থ্য সচিব ফোন করেছেন মোফাখখারুল ইসলামকে, যে মোফাখখারুল ইসলাম তাঁর অধ্যক্ষ-কক্ষে ডেকে নিয়ে একটি উড়ো চিঠির ওপর ভিত্তি করে আমাকে কী জঘন্য অপমানটাই না করেছিলেন। আমার মত নিরীহ মানুষ কোনওদিন শোধ নিতে পারেনি সেই অপমানের। তবে আমার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রী বা স্বাস্থ্য সচিবের উতলা হওয়াটিই তাঁকে অন্তত এইটুকু বুঝিয়েছে যে আমি নিতান্তই একটি তুচ্ছ জীব নই, যে রকম জীব ভেবে তিনি ঘৃণায় আমাকে মাটির সঙ্গে থেতলে ফেলতে চাচ্ছিলেন। এইটিই আমার শোধ। এর চেয়ে ভাল শোধ আর কী হতে পারে! চড়ের বদলে চড় দেওয়া আমি পছন্দ করি না, শারীরিক পীড়নের চেয়ে মানসিক পীড়ন ঢের বেশি যন্ত্রণা দেয়। স্বাস্থ্য সচিব ইমরান নূর মোফাখখারুল ইসলামের কাছ থেকে আমার ফোন নম্বর নিয়ে আমাকে ফোন করেছিলেন, অনুরোধ করেছেন আমি যেন প্রেসিডেণ্টের সাদর আমন্ত্রণটি রক্ষা করি। আমি রক্ষা করিনি।
শান্তিবাগের বাড়িটি সাজিয়ে নিয়েছি খুব সুন্দর করে। আরমানিটোলার বাড়িটির সঙ্গে শান্তিবাগের বাড়ির তুলনা হয় না। ও বাড়িটি ছিল বস্তির বাড়ি, এ বাড়ি আধুনিক, ঝকঝকে। ড্রইং কাম ডাইনিং। দুটো বাথরুম। দুটো বেডরুম। বারান্দা। আধুনিক কিচেন। বাড়িটি যেমন সুন্দর, পরিবেশও চমৎকার। আরমানিটোলার তুলনায় শান্তিবাগের সংসার অনেক য়চ্ছল। অবশ্য এই য়চ্ছলত!টুকু দিতে পরিশ্রমও করতে হয়। মাইনেতে বাড়িভাড়া কুলোয় না, সুতরাং কলাম লিখে টাকা রোজগার করতে হয়। যদিও লেখা থেকে ডাক্তারি চাকরির চেয়ে বেশি আয় হয়, তবু লেখার চেয়ে ডাক্তারি চাকরিতে সময় যায় কয়েকশ গুণ বেশি। লেখা আজ লোকে চাইছে, কাল হয়ত চাইবে না। চাকরিটিই তখন ভরসা। ভরসার জায়গাটি হেলাফেলায় নষ্ট করি না মোটেও। একটি কলামে কখনও তিনশ টাকা, কখনও পাঁচশ টাকা আসে, মাসে দশটি কলাম লিখলে বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎ খরচ হয়ে যায়। মাইনের টাকায় বাজার খরচা আর রিক্সাভাড়া চলে। দশটির বেশি কলাম লিখলে নাটক থিয়েটার দেখে বই পত্র কিনে বেশ চলে যায়। তবে সবসময় যে এই নিয়মে সবকিছু চলে তা নয়, কখনও কোনও পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়, কোনও পত্রিকার মালিক বদলে যায়, নতুন মালিক আমার লেখা আর ছাপতে চায় না অথবা পত্রিকার টাকা ফুরিয়ে যায়, অথবা টাকা দেবে কথা দিয়েও কেউ হয়ত দেয় না। তারপরও আমি পিছু হটি না। আমি হার মানি না। অন্য কারও হাতে নিজেকে সমর্পণ করি না। মিলন মাঝে মাঝে সেও এটা সেটা বাজার করে। আর মা রান্নাঘর সামলালে তো খরচ বড় রকম বাঁচিয়ে চলেন। নিজে তলে তলে কৃচ্ছউস!ধন করে এই কাজটি করেন। শান্তিবাগের সব ভাল, তবে মিটফোর্ড হাসপাতালটি দূরে পড়ে যায়, এই যা সমস্যা। আরমানিটোলা থেকে হেঁটেই হাসপাতালে যাওয়া যেত। এখান থেকে রিক্সা নিতে হয়। রিক্সা গুলিস্তানের ট্রাফিক জ্যামে পড়ে আধঘণ্টা একঘণ্টা বসে থাকে।
শান্তিবাগের বাড়িতে অতিথির আগমন অনেক বেশি। কবি বন্ধু, ডাক্তার বন্ধু, ভক্তকূল, আত্মীয়কূলের কেউ না কেউ আসছেই। শান্তিবাগের বাড়িটি সত্যিকার যাকে বলে হোম, সুইট হোম। যে অবকাশের টান কোনও দিনই অবকাশ ছেড়ে যেখানেই থেকেছি, কমেনি, এই শান্তিবাগের শান্তি আমার অবকাশের মোহ অনেক কমিয়ে দেয়। তাছাড়া একটি তো চ্যালেঞ্জ আছেই, আমি স্বনির্ভর হব এবং একা থাকব, কোনও স্বামী নামক প্রভু পুরুষ আমার আশেপাশে থাকবে না, আমি হব আমার নিয়ন্ত্রক, যেভাবে আমি জীবন যাপন করতে পছন্দ করি, সেভাবে করব, কেউ আমাকে বলবে না এটা কর, ওটা কর। কারও কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে না কিছুর জন্য। ঠিক এরকম জীবনই আমি তো চেয়েছিলাম। সম্পূর্ণ একটি স্বাধীন জীবন। বাবার অধীন থেকে, স্বামীর অধীন থেকে মুক্ত একটি জীবন। এই জীবনটি অর্জন করতে আমাকে কম পথ পেরোতে হয়নি। স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করার স্বপ্ন সাধকে আমি খুব অনায়াসে এখন ছুঁড়ে ফেলতে পারছি। তুলোর মত উড়ে যাও স্বপ্ন। এই স্বপ্ন আমার জন্য নয়। এই স্বপ্ন লালন করে নিজেকে কম অপদস্থ করিনি। স্বপ্ন তুমি ভেসে যাও বুড়িগঙ্গার জলে, তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। স্বপ্ন তোমাকে মাটির তলায় পুঁতে দিচ্ছি, তুমি মরে যাও। স্বপ্ন তুমি আমার আঙিনামুক্ত হও, আমার হৃদয়মুক্ত হও। আমাকে আর নাশ করতে এসো না কখনও। এক স্বপ্ন চলে গেলে অন্য স্বপ্ন আসে। স্বপ্ন তো কত রকম হতে পারে। আমার এখন অন্য রকম স্বপ্ন। এই স্বনির্ভরতাটুকু, নিজের এই স্বাধীনতাটুকু নিয়ে বাকি জীবন বেঁচে থাকবার স্বপ্ন। এখন বড় নির্ভার লাগে, বড় দুঃস্বপ্নমুক্ত লাগে। যেন দীর্ঘ একটি দুঃস্বপ্নের রাত পার হয়ে এখন দেখছি চারদিকে আলোয় ঝলমল সকাল। যেন ঘুমিয়ে ছিলাম, ঘুমের মধ্যে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। জেগে উঠেছি। দীর্ঘ দীর্ঘ কাল একটি অন্ধকার গুহার ভেতরে আটকা পড়ে ছিলাম, অন্ধকারই আমার জীবন আর জীবনের স্বপ্নগুলো নিয়ন্ত্রণ করত। আলোর কোনও ঠিকানা আমার জানা ছিল না। নিজে আলো খুঁজে খুঁজে বের করেছি, আলো আমি ছড়িয়ে দিই চাই আর যারা অন্ধকারে আছে, তাদের দিকে। অন্ধকারে পড়ে থেকে স্যাঁতসেঁতে জীবন কাটাচ্ছে যারা, তাদের দিকে একটি হাত বাড়াতে চাই, যে হাতটি ধরে তারা উঠে আসতে পারবে আলোর মিছিলে। আমার হাত কি তেমন কোনও শক্ত হাত! শক্ত নয় জানি, তবু তো একটি হাত! এই একটি হাতই বা কে বাড়ায়!
আমার জীবনে অভাবিত কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে। বাংলাবাজারের প্রকাশকরা ভিড় করেন আমার বাড়িতে। সকলের প্রশ্ন আমি কি পণ করেছি বিদ্যাপ্রকাশকে ছাড়া আর কোনও প্রকাশককে বই দেব না! এরকম পণ আমি নিশ্চিতই করিনি। খোকা আমার বই ছাপেন কিন্তু আমাদের মধ্যে এরকম কোনও চুক্তি হয়নি যে অন্য প্রকাশকেকে বই দেওয়া যাবে না। তাহলে বই দিন। আজই দিন। আশ্চর্য বই কোত্থেকে দেব! যা লিখেছি কবিতা। বিদ্যাপ্রকাশ থেকে সবই ছাপা হয়ে গেছে। যা কলাম ছাপা হয়েছে পত্রিকায়, সব বই হয়ে বেরিয়ে গেছে। তা হলে লিখুন। একটি উপন্যাস লিখুন। উপন্যাস! পাগল হয়েছেন! উপন্যাস আমি লিখতে জানি না। জীবনে কখনও লিখিনি। জীবনে কখনও না লিখলেও এখন লিখুন। খোকার কাছেও তাঁর প্রকাশক বন্ধুরা অনুরোধ নিয়ে যাচ্ছেন। খোকাও একদিন আমাকে বললেন তাঁর বন্ধু অনন্যা প্রকাশকের মুনিরকে যেন একটি বই দিই, শিখা প্রকাশনীর লোককে নিয়ে এলেন, তাকেও বই দিতে হবে। আবার একদিন আফসার ব্রাদার্সএর প্রকাশককে নিয়ে এলেন, একেও কিছু না কিছু দিতে হবে। উপন্যাস না দিলেও যেন গল্পের বই দিই, তা না হলে যেন কবিতা, বেশি যদি না দিতে পারি, অন্তত দশটি কবিতা, দশটি না হলেও পাঁচটি, শিল্পীকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে কবিতা কার্ডের প্যাকেট করবেন। যে ব্যপারটি ঘটে, তা হল অগ্রিম টাকা দিয়ে যান প্রকাশকগণ। রয়্যালটির টাকা পেতে কখনও অভ্যস্ত নই আমি। খোকা আমার ভাই বন্ধু শুভাকাঙ্খী, বাড়িতে এলে খালি হাতে আসেন না, নানা রকম ফল মিষ্টি বিস্কুট চানাচুর ইত্যাদি নিয়ে আসেন, কখনও কখনও হঠাৎ কোথাও বেশি খরচ করে একেবারে কপর্দকহীন হয়ে গেলে খোকা কিছু টাকা রেখে যান। সে তো প্রয়োজনে, শখের ব্যপারটিও দেখেন তিনি, লেখার টেবিলের জন্য সুন্দর একটি চেয়ার পছন্দ করেছিলাম, কিন্তু টাকা ছিল না বলে কিনতে পারিনি, খোকা সেটি কিনে একদিন বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রয়্যালটির হিসেব কখনও আমাকে দেননি। হিসেব আমি চাইও নি। চাইনি লজ্জায়। তাছাড়া খোকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হিসেবের সম্পর্ক নয়। যে কোনও প্রয়োজনে কোনও রকম দ্বিধা ছাড়াই আমি খোকাকে ডাকতে পারি, খোকা সব ফেলে ছুটে আসেন। কোনও টাকা দিয়ে এই সহানুভূতি কেনা যায় না। রয়্যালটির টাকা ব্যপারটি আসলেই বড় লজ্জার, যখন অনন্যা বা শিখা প্রকাশনীর লোক টাকা বাড়াল, আমার কান নাক সব লাল হয়ে গেল মুহূর্তে। টাকা হাতে নিতেও এমন লজ্জা হচ্ছিল যে হাত পেছনে গুটিয়ে রেখেছিলাম। প্রকাশকরা টাকা টেবিলে রেখেছেন নয়ত খোকার হাতে দিয়েছেন আমাকে দেওয়ার জন্য। অগ্রিম রয়্যালটির টাকা। অবশ্য টাকা দেওয়ার আগে আমি অনেক বলেছি, টাকা দেবেন না, বই তো লিখি নি। বই লিখিনি তাতে কারওর আপত্তি নেই। টাকা থাকুক, যখন লেখা শেষ হবে, এসে নিয়ে যাবেন। লিখতে যদি এক বছর লাগে? তা লাগুক। যদি পাঁচ বছর লাগে? তাতেও নাকি ক্ষতি নেই। টাকার দরকার নেই আমার। দরকার না থাকলেও যেন আমি রেখে দিই। বই লিখে নিই, ছাপা হোক, বিক্রি হয় কি না দেখুন, তারপর তো রয়্যালটি। প্রকাশকরা আমার কথা মানেন না, বলেন বই প্রকাশের পর তো রয়্যালটি পাবোই, তার আগেও টাকাটা থাকুক। টাকা থাকে। এত টাকা এক সঙ্গে কখনও দেখিনি আগে। শুনেছি এক হুমায়ুন আহমেদকেই রয়্যালটির টাকা বই লেখার আগেই দেওয়া হয়। এখন আমাকেও! মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা। শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা বইটির পরিবেশনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নসাস প্রকাশনীকে। নসাস প্রকাশনী বইটি বিলি করার কোনও রকম আগ্রহ প্রকাশ করেনি। দুবছর পর নসাসের গোডাউনে পড়ে থাকা পোকায় খাওয়া বই নিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। দ্বিতীয় বইটি প্রকাশের জন্য যে অনিন্দ্য প্রকাশনের নাজমুল হকের দ্বিধা ছিল, নিশ্চয়ই সেই নাজমুল হক আমার বই ছাপার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন এখন। আমি খুব ভাল করেই জানি আজ যে প্রকাশকরা করজোড়ে বই এর জন্য অনুরোধ করছেন, একসময় তাঁরাই হয়ত নাক সিটকোতেন নাম শুনলে। আমাকে লিখতে হয় প্রকাশকদের চাপে। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে বসে রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে লিখি। বাড়িতে অতিথি এলে সময় দিতে হয়। সংসারে এটা নেই তো ওটা নেই, সেগুলোও দেখতে হয়, একশ একটা কাজের ফাঁকে ফাঁকে লিখি। লেখা আদৌ কিছু হয়েছে কি না তা ভাবার আগেই প্রকাশক এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যান। প্রায় প্রতিদিন তাগাদা দেন, কতদূর হয়েছে লেখা, দেখি! হচ্ছে হচ্ছে হবে হবে করে করে সময় পার করি। সময় প্রকাশনের ফরিদ আমার বাড়ি এসে দিনের পর দিন অনুরোধ করে গেছেন, তাঁকে দিই অপরপক্ষ নামের একটি উপন্যাস। অনন্যাকে শোধ নামে একটি উপন্যাস দিই, উপন্যাস না বলে উপন্যাসিকা বলা উচিত অথবা বড় গল্প। গাইনিতে কাজ করে হাত দক্ষ হয়েছে হয়ত, এতদিনে অ্যানেসথেসিয়া দিতে দিতেও হাত পেকেছে, উপন্যাস লেখার জন্য মোটেও কিন্তু হয়নি। সভয়ে সলাজে লিখে শেষ করি। মনে খুঁতখুঁতি থেকেই যায়। লেখাগুলোয় একটি বক্তব্য অন্তত দাঁড় করাতে পেরেছি, নারীর শরীর এবং হৃদয় সবই যে তার নিজের, এসব অন্য কারও সম্পত্তি নয়, এক একটি নারীর জীবন বর্ণনা করে তা বলেছি। খোকার জন্য নতুন কলামের বই নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য আর বালিকার গোল্লাছুট নামে একটি কবিতার বই। কবিতাতেও দেখেছি আমি, কেবলই নারীর কথা। নারীর সুখের কথা, কষ্টের কথা, নারীর পায়ের নিচের মাটির কথা, শেকল ছেঁড়ার কথা, সমাজের রাষ্ট্রের পরিবারের নিয়মগুলো ভেঙে বেরিয়ে আসার কথা। মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচার কথা। জীবনে হোঁচট খেতে খেতে জীবনের যে মর্মান্তিক রূপ দেখেছি, জীবনে স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্নের যে ভাঙন দেখেছি, তারপরও যে আবারও স্বপ্ন রচনা করেছি, আবারও যে উঠে দাঁড়িয়েছি এবং ক্লান্ত রক্তাক্ত জীবনের যে অভিজ্ঞতাই জীবনের রাজপথে, পথে, অলিতে, গলিতে সঞ্চয় করেছি তার সবই কবিতা, কলাম, উপন্যাস যা কিছুই লিখি না কেন, আমার অজান্তেই রক্ত ঝরার মত করে ঝরে কলমের নিব থেকে।
আমার দিনগুলো অদ্ভুত রকম পাল্টো যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সংশয় জাগে এ সত্যিই আমি তো! ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের লজ্জাবতী ভীতু কিশোরীটি তো! মাঝে মাঝে আমার বিশ্বাস হয় না অনেক কিছুই। বিশ্বাস হয় না যে টেলিভিশনের প্রযোজিকা আমার বাড়ি এসে গান লিখিয়ে নিয়ে যান, আর সেই শৃঙ্খল ভাঙার গান দেশের জনপ্রিয় গায়িকা সামিনা নবী গান টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে। এ অবশ্য প্রথম নয়, আগেও আমার কবিতাকে গান করা হয়েছে। সুর দিয়েছে ইয়াসমিন। সঙ্গী সাথী নিয়ে ইয়াসমিন সেসব গান গেয়েছে মঞ্চে। কিন্তু সে তো ময়মনসিংহে। ঢাকা শহরে, তার ওপর ঢাকার টেলিভিশনে যেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ সেখানে আমার মত সাধারণের কবিতা বা গান টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো হবে তা কি আমি কখনও ভেবেছিলাম! বিখ্যাত গায়ক ফকির আলমগীর আমাকে গান লেখার জন্য তাগাদা দেন। তাঁর জন্যও গান লিখতে হয় আমাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা আসেন আমার কাছে, আমার কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে বড় একটি এনথলজি বের করছেন, ওতে দেবেন। ব্রিটিশ কাউন্সিলে ডাকেন আমাকে কবিতা পড়ার জন্য। নারী সংস্থার নেষনীরা আসেন তাঁদের অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে। অনন্যা পত্রিকা থেকে বছরের সেরা দশ নারী নির্বাচন করা হয়েছে, এবং তাদের সম্মানিত করা হয়েছে চমৎকার অনুষ্ঠান করে, সেরা দশ নারীর মধ্যে একজন আমি। ঢাকায় তো আছেই, ঢাকার বাইরে থেকেও লোক আসে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে বিভিন্ন সাহিত্য অনুষ্ঠানে, বইমেলায়। টেকনাফ থেকে ডাক্তার মোহিত কামাল ঢাকায় আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। মোহিতের ইচ্ছে টেকনাফে তার প্রিয় দুই লেখক ইমদাদুল হক মিলন এবং তসলিমা নাসরিনকে সে সম্বর্ধনা দেবে। টেকনাফের কচি কাঁচার মেলার সে সভাপতি, মেলা থেকেই সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। মোহিত সাহিত্য অনুরাগী, আমারই সমবয়সী, খোকার সঙ্গে পরিচয় হয় তার, কি করে কি করে খোকার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। টেকনাফে ফিরে গিয়ে খোকার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করে এই ব্যবস্থাটি মোহিত পাকা করে। খোকা আমাকে আর মিলনকে নিয়ে টেকনাফে রওনা হন। দেশের আনাচ কানাচে কত কিছু দেখার আছে, আমার দেখা হয়নি দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলই। দূরে কোথাও যাওয়ার জন্য আমি এক পায়ে খাড়া। টেকনাফে, দেশের দক্ষিণের শেষ বিন্দুটিতে পৌঁছে খুব আনন্দ হয় আমার। মোহিতের বাড়িতে অতিথি হই আমরা সবাই। অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় দুই লেখককে। সম্বর্ধনা পেয়ে আমি অভ্যস্ত নই, শরমে মুখ তুলতেই পারিনি। দুই লেখককে দিয়ে কচি কাঁচাদের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কারও দেওয়ানো হয়। অনুষ্ঠানের পর মোহিত আমাদের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ আর মহেশখালি দ্বীপে বেড়াতে নিয়ে যাবার আয়োজন করল। ভযাবহ যাত্রা। মাছ ধরার ট্রলারে বসে আছি, উত্তাল সমুদ্রের এক স্রোত ট্রলার ডুবিয়ে নেয়, আরেক স্রোত ভাসায়, ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে প্রবাল- দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে পৌঁছি। আশ্চর্য সুন্দর একটি দ্বীপ। উঁচু উঁচু বাঁশের ঘরে কিছু মানুষ বাস করে। চারদিকে অচেনা সব গাছগাছালি। সমুদ্রের য়চ্ছ সবুজ জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটি। সেন্ট মার্টিন থেকে মহেশখালি দ্বীপেও গিয়ে জেলেদের জীবন দেখি, জলই এই জেলেদের বাঁচাচ্ছে, জলই এই জেলেদের মারছে। জলকে ভালবাসে, আবার জলের সঙ্গেই যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে এরা। সমুদ্রের তীরে চমৎকার সময় কাটিয়ে ফিরে আসি ঢাকায়। টেকনাফে মিলন ছিল, সাধারণ এক লেখক-বন্ধুর মতই সে ছিল। মিলনের জন্য অন্যরকম কোনও আবেগ আমি অনুভব করিনি। কাশ্মীরের কিছু স্মৃতি আছে সুখের, তা থাক। স্মৃতি স্মৃতির জন্যই। এর পরের আমন্ত্রণ সিলেটে। সিলেটের বইমেলায়। এবারও খোকা ব্যবস্থা করেন সিলেট যাত্রা। আমি, খোকা, অসীম সাহা যাত্রা করি। সময় প্রকাশনের ফরিদ তাঁর বউসহ আমাদের সঙ্গী হন। সিলেটেও খুব ভাল সময় কাটে। বইমেলায় অটোগ্রাাফ শিকারির ভিড়ে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাই। এই সুদূর সিলেটেও লোকে আমার লেখা পড়ে! দেখে আমি অভিভুত। সিলেটের চা বাগানে ঘুরে, তামাবিলে শিলং পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝর্নার স্রোত এসে নদীতে পড়েছে, সেই নদীর য়চ্ছ সুন্দর জলের পাথরকুচির ওপর খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে আমি অপূর্ব রূপ দেখি প্রকৃতির। ওপারেই ভারত, হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় এমন দূরে। অথচ একটি কাঁটাতার বসানো মাঝখানে। এই বাধাটি দেখে বেদনায় নুয়ে থাকি। এখানের গাছ থেকে ফুল পাতা ঝরে পড়ছে ওখানের মাঠে। ওখানের পাখি উড়ে এসে বসছে এখানের গাছে, কেবল মানুষের অধিকার নেই দুকদম সামনে হাঁটার। আমরা এই পৃথিবীর সন্তান, আমরা কেন যতদূর ইচ্ছে করে হাঁটতে পারবো না এই পৃথিবীর মাটিতে, কেন সাঁতার কাটতে পারবো না যে কোনও নদী বা সমুদ্রে? মানুষই মানুষের জন্য রচনা করেছে অসভ্য শৃঙ্খল। সীমান্তের কণ্টক থেকে একটি কণ্টক এসে হৃদয়ে বেঁধে।
আমন্ত্রণ আসতে থাকে আরও বড় শহর থেকে, আরও বড় বড় সাহিত্য অনুষ্ঠানে। আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। প্রধান অতিথির সম্মান দেওয়া হয়। মঞ্চের পেছনের বড় পর্দায় বড় বড় করে লেখা থাকে আমার নাম। ঢাকায় নাট্যসভা থেকে সাহিত্য পুরষ্কারও দেওয়া হল, শামসুর রাহমান আর আমি পাই পুরস্কার। শহিদুল হক খান পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি করলেন জাতীয় যাদুঘরের মিলনায়তনে। শহিদুল হক নাটক লেখেন, নাটক পরিচালনা করেন আবার নাট্যসভা নামে একটি সংগঠনও করেন। প্রতিভা আছে লোকটির। লোকে বলে বড় শঠ লোক, আমি অবশ্য তার শঠতা দেখিনি নিজ চোখে। আমার সঙ্গে অসম্ভব আন্তরিক তিনি।
কবি সাহিত্যিকরা ঘন ঘন আসেন আমার বাড়িতে, পুরো বিকেল জুড়ে আদা-চা খেতে খেতে আড্ডা জমে। শামসুর রাহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে আমার। দীর্ঘ দীর্ঘক্ষণ আড্ডা হয় সাহিত্য নিয়ে রাজনীতি নিয়ে। লেখক রশীদ করিম শামসুর রাহমানের বিশেষ বন্ধু। তাঁর বাড়িতে আমাকে আর শামসুর রাহমানকে প্রায়ই তিনি ডাকেন সাহিত্যের আলোচনা করতে। সাহিত্য নিয়ে হয়, ধর্ম নিয়েও আমাদের কথা হয়, আমি আর শামসুর রাহমান ধর্মহীনতার পক্ষে, রশীদ করীম ধর্মের পক্ষে। পক্ষে হলেও তিনি একজন সুসভ্য সুশিক্ষিত সুসাহিত্যিক। এই যে আমাকে দেশের বড় বড় সাহিত্যিকরা স্নেহ করেন সে আমি অল্প বয়সী (তাঁদের বয়সের তুলনায়), সুন্দরী (!) মেয়ে বলে নয়, আমার লেখার কারণে করেন। আমার কবিতায় গদ্যে আমার বক্তব্যে তাঁরা নতুন প্রজন্মের নতুন দিনের একটি সম্ভাবনা দেখছেন বলে করেন। আমার লেখা তাঁরা পড়েন, আলোচনা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে আমি খুব প্রয়োজনীয় কথা লিখছি। আমার সমবয়সী সাহিত্যিকদের চেয়ে আমার দ্বিগুণ ত্রিগুণ বয়সী সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার চলাফেরা বেশি হতে থাকে। শিল্প সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি এসব তো আছেই, মানবিক দিকটিও অপ্রধান নয়। যেদিন আমাকে শামসুর রাহমান খবর দিলেন যে রশীদ করিম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আমি হাসপাতাল থেকে ছুটে গিয়ে রশীদ করিমকে বাড়ি থেকে দ্রুত তুলে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ভর্তি করিয়ে দিই। রশীদ করিম বেঁচে যান কিন্তু মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায় শরীরের অর্ধেকটা অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। হাসপাতাল থেকে তিনি বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর তাঁকে দেখতে, সঙ্গ দিতে, তাঁর মন ভাল করে তুলতে আমি আর শামসুর রাহমান দুজনই তাঁর বাড়িতে যাই। শামসুর রাহমানের সঙ্গে পান্না কায়সারের ভাল বন্ধুত্ব। ইস্কাটনে পান্না কায়সারের বাড়িতেও আমরা যাই পানাহার আর আড্ডার নেমন্তন্নে। পান্না কায়সার আর আমি যশোরের সাহিত্য সভায় গিয়েছিলাম। লেখক শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার নিজেও উপন্যাস লিখছেন, রাজনীতির মঞ্চে তিনি কথা বলে অভ্যস্ত, চমৎকার বক্তৃতা করলেন যশোরে। নতুন শহর দেখে, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভাল লাগে আমার কিন্তু মঞ্চে যখন আমাকে ঠেলে দেওয়া হয় বক্তৃতা করতে, আমি দর্শক শ্রোতা কাউকে মুগ্ধ করতে পারি না, বক্তৃতা করতে হলে কিছু শক্ত শক্ত শব্দ ব্যবহার করতে হয়, সেই শব্দগুলো আমি কখনও আয়ত্ত্ব করতে পারি না।
বেইলি রোডে চরমপত্রের নরম লোক এম আর আখতার মুকুলের বইয়ের দোকান সাগর পাবলিশার্সে বই কিনতে গেলে প্রায়ই দেখি শওকত ওসমান বসে আছেন ওখানে। আমাকে দেখেই খলবল করে রাজ্যির কথা বলেন। দেশের কত বড় একজন সাহিত্যিক। একদিন আমার নামের অর্থ করে দিলেন। তার পর দেখি তিনি ফটোকপি করে বিলোচ্ছেন আমাকে নিয়ে লেখা তাঁর একটি কবিতা। নাসরিন নামের অর্থ বন্য গোলাপ, কমতি হয় না তাই সুগন্ধের তাপ।পাওয়ার একটি সীমা আছে। আমার পাওয়া সীমা ছাড়িয়ে যায়।
দেশের জনপ্রিয় কবি নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে আমার খুব চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তিনি বাড়ির লোকের মত আপন হয়ে ওঠেন। গুণের চরিত্রের একটি সাংঘাতিক দিক আছে, তিনি কোনও অপ্রিয় সত্য কথা বলতে কোনও দ্বিধা করেন না, লোকে কি বলবে তা নিয়ে ভাবেন না। শুধু বলে তিনি ক্ষান্ত নন, জীবনে তিনি তা করেও দেখান। গুণের হুলিয়া কবিতাটি পড়ে যে কোনও পাঠকের মত আমিও ভেবেছিলাম, গুণের বিরুদ্ধে বুঝি কোনও রাজনৈতিক মামলার হুলিয়া জারি হয়েছিল। একদিন জানতে চেয়েছিলাম হুলিয়া জারি হওয়ার পর তিনি কি করে গা ঢাকা দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছিলেন কি না এসব নিয়ে, তখনকার নিষিদ্ধ বাম রাজনীতির রোমহর্ষক কাহিনী বা পাকিস্তানী সরকারের বিরুদ্ধে কোনও গোপন আন্দোলনের কথা শুনব বলে কান মন সব সজাগ রেখে বসেছি, গুণ তখন অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললেন যে তিনি ডাকাতির মামলার আসামী ছিলেন। সত্যি সত্যিই ডাকাতির মামলা। কোনওরকম সংকোচ না করে বলে দিলেন ঘটনা, নেত্রকোনার এক গ্রামে এক রাতে তিনি সত্যিকার ডাকাত দলের সঙ্গে ভিড়ে ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন। কেন ডাকাতি? খুব সরল জবাব, টাকার দরকার ছিল। টাকার দরকার জীবনে প্রচুর এসেছে গুণের। আনন্দমোহন কলেজের হোস্টেলে থাকাকালীন হোস্টেলের ক্যাপ্টেন হয়ে তিনি বাজার করার টাকা থেকে চুরি করতেন টাকা। নতুন শার্ট কিনেছিলেন সে টাকায়। হোস্টেলের ঘরে রাতে রাতে জুয়ো খেলতেন। ধরা পড়ে যাওয়ার পর তাঁকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। ঢাকায় যখন বাস করতে শুরু করলেন, কবিতা লিখে টাকা যা রোজগার করেন, তাতে জীবন চলে না। ক্ষিধে পেটে হাঁটেন, পকেটে পয়সা নেই। এরকম অনেক হয়েছে যে হাতে কোনও টাকা পয়সা ছাড়াই রেস্তোরাঁয় ঢুকে ভাত খেয়েছেন। এরপর মার খাবার ভয়ে পালানোর মতলব করেছেন। পানি নিয়ে বারান্দায় হাত ধুতে যাবার ভান করে পানির গেলাস ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। রেস্তোরাঁর লোক পেছনে দৌড়েও রবীন্দ্রনাথের মত দেখতে লম্বু গুণের টিকি দাড়ি কিছুই ছুঁতে পারেনি। খেয়ে পয়সা না দিয়ে ঝড় বৃষ্টি কিছু মানেননি, দৌড়ে পালিয়েছেন। এসব বলতে গুণের আসলেই কোনও সংকোচ হয় না। তাঁর এই সংকোচহীনতা আমাকে মুগ্ধ করে। নিজেকে নিয়ে কোনও রকমের অহংকার না করে বরং প্রাণখুলে এমন রসিকতা করতে আমি আর কাউকে দেখিনি আগে। আমার যখন দশ বছর বয়স, ইশকুলের নতুন ক্লাসে উঠেছি, বাবা আমাকে নতুন ক্লাসের সব বই কিনে দেননি তখনও। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে ওদিকে। ক্লাসে মেয়েরা নতুন নতুন বই নিয়ে আসছে। আমার চেয়ে বেশি বই তাদের। তখন ছুটির পর দেখি আভা রুদ্র নামে ক্লাসের একটি মেয়ে ভুলে তার বাংলা দ্রুতপঠনের গল্পের বইটি ফেলে চলে গেছে। আমিই সবচেয়ে শেষে বেরিয়েছিলাম ক্লাস থেকে। আভা রুদ্রর বেঞ্চে পড়ে থাকা বইটি হাতে নিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বইটির লোভ সামলাতে না পেরে আমি পাজামার মধ্যে বইটি গুঁজে নিয়েছিলাম। ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটছি আর বুক কাঁপছে। পেটে বই। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল জামার তলের বইটি বুঝি যে-ই আমার দিকে তাকাচ্ছে দেখে ফেলছে। গেটের কাছে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। আভা রুদ্রও দাঁড়িয়ে আছে। ওর বইটি আমার পেটে, আমার ইচ্ছে করছিল বইটি পেট থেকে বের করে তাকে দিয়ে দিই। কিন্তু পেট থেকে বইটি তখন ভরা মাঠে আমি বের করি কি করে! পেটে বই নিয়েই হেঁটে বাড়ি ফিরেছি। বুক ধড়ফড় তখনও থামেনি। তোশকের তলে লুকিয়ে রেখেছিলাম বইটি, কেউ যেন টের না পায় বইটি আমি চুরি করে এনেছি। বইটি পেটে করে গোসলখানায় নিয়ে, ছাদে নিয়ে পুরোটাই পড়ে ফেলি পরদিনই। দুদিন পর বাবা আমাকে বাকি পাঠ্য বইগুলো কিনে দিলেন, দ্রুতপঠন বইটি অবশ্যই ছিল। ইশকুলে গিয়ে আভা রুদ্রকে দেখে আমার বুক ভেঙে যায়। হারিয়ে যাওয়া বইটির জন্য সে কান্নাকাটি করছে, ক্লাসের সবাইকে জিজ্ঞেস করছে তার বইটি কেউ দেখেছে কিনা। তাকে আমি বইটি ফিরিয়ে দিতে পারছি না, ফেরত দিলে সে আমাকেই গাল দেবে চুরি করেছিলাম বলে। এদিকে মন খুব খারাপ আমার, নিজেকে চোর বলে মনে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। রাতে ঘুম আসে না, এপাশ ওপাশ করি। কাউকেই নিজের এই চুরির কথাটি বলতে পারি না। ওই চিকন বইটি আমার কাঁধে গারো পাহাড়ের মত এমন ভারী হয়ে বসেছিল যে একদিন পেটে করে বইটি নিয়ে সকাল সকাল ইশকুলে গিয়ে ক্লাসঘরে কেউ না ঢোকার আগেই ঢুকে আভার ডেস্কের ওপর রেখে দিয়ে ভারমুক্ত হই। পরে আভার সঙ্গে আমার ভাল বন্ধুত্ব হয়েছিল। কোনওদিন তাকে বলিনি বই চুরির কথা। বড় হবার পরও কোনও দিন কাউকে বলিনি। বইটি গোপনে ফেরত দিয়েও চুরি করার অপরাধবোধ থেকে মুক্তি আমি পাইনি। নির্মলেন্দু গুণ, আমি জানি, এরকম অপরাধের কথা অনায়াসে বলে ফেলতে পারেন। নির্মলেন্দু গুণের চুরি ডাকাতি জুয়োখেলা এসব আমি পছন্দ না করলেও তাঁর স্বীকারোক্তি আমি পছন্দ করি। নিজের অংসযম নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন অনেক, তাঁর বেশ্যাগমন নিয়ে তিনি কোনও রাখঢাক করেননি। মেডিকেলের ছাত্রী নীরা লাহিড়ির সঙ্গে গুণের বিয়ে হয়েছিল। কবি আর হবু ডাক্তারের সুন্দর সংসার, কন্যা মৃত্তিকা জন্মেছে। কবি ব্যস্ত অর্থ উপার্জনে, হবু ডাক্তার ব্যস্ত ডাক্তারি বিদ্যা অর্জনে। মৃত্তিকাকে দেখাশোনা করার জন্য নেত্রকোনা থেকে গীতাকে আনা হয়েছে। গীতার নিজের কোনও বাচ্চা কাচ্চা নেই, মৃত্তিকাকে সে পরম আদরে লালন করছে। এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন গুণের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললেন নীরা। বিয়ে ভেঙে নীরা তাঁর কন্যা নিয়ে চলে গেলেন। নির্মলেন্দু গুণ গীতাকে নিয়ে একা পড়ে রইলেন। ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় এসে বস্তিতে বাস করছেন কেবল গীতাকে নিয়ে নয়, গীতার জ্ঞাতিগুষ্ঠি নিয়ে, সবারই দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। নীরা দেখেশুনে একটি ডাক্তার ছেলেকে বিয়ে করে নিয়েছেন। মৃত্তিকা থাকে তাঁর দিদিমার বাড়িতে। গুণ থাকেন মৃত্তিকার ধারে কাছেই বস্তিতে। বস্তিতে থাকা নিয়ে বা গীতার গুষ্ঠি পালন করা নিয়ে গুণকে কোনও দুঃখ প্রকাশ করতে দেখিনি। তিনি সুখী। অভাব আছে কিন্তু অভাবের বোধ নেই। জীবনের প্রতি বিন্দু তিনি উপভোগ করেন। প্রাণ খুলে হাসেন, বুক খুলে ভালবাসেন, হাত খুলে লেখেন। ধন দৌলতের কোনও মোহ নেই। বিলাস ব্যসনের কোনও সাধ নেই। বিলাস বহুল বাড়ির বিলাস বহুল খাবার-টেবিলে সুস্বাদু সব উপাদেয় খাবার খেতে পারেন আবার বস্তির মাটির উঠোনে বসে মাছি তাড়াতে তাড়াতে নেড়ি কুত্তা খেদাতে খেদাতে বাসি ডাল ভাতও খেতে পারেন। দুটোতেই তাঁর সমান তৃপ্তি। লাস ভেগাসের ক্যাসিনোয় বসেও কয়েক হাজার ডলারের জুয়ো খেলে যে সুখ পান, ঢাকার কোনও ঘিঞ্জি গলিতে বসে দু পাঁচ টাকা নিয়ে জুয়ো খেলেও তাঁর একই সুখ। নির্মলেন্দু গুণ যে চোখে জীবন দেখেন, সে চোখটি বড় নির্মোহ কিন্তু বড় অভিজ্ঞ চোখ। বিশাল বিশ্ব ব্রম্মাণ্ডে জীবন হল সরু সুতোর মত, যে সুতোটি টান টান হয়ে আছে যে কোনও মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে বলে, সেই সুতোর ওপর নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে জীবনের রস সন্ধানে এবং পানে তিনি কোনও কার্পণ্য করেন। আড্ডা দিতে দিতে একদিন অনেক রাত হয়ে যাওয়ায়, সেদিন মিলন, মা কেউ ছিল না বাড়িতে, বাড়তি ঘর আছে, বিছানা আছে, গুণকে বলেছি রাতে থেকে যেতে। তিনি থেকে গেলেন। ভোরবেলায় দেখি গীতা এসে হাজির। দাদা রাতে বাড়ি ফেরেননি, পাতি পাতি করে শহর খুঁজে শেষে আমার ঠিকানা যোগাড় করে এখানে দেখতে এসেছে গুণ আছেন কি না।
গীতা গুণকে দেখেই বলল, ‘দাদা, আপনে কেমন মানুষ গো! আমরা চিন্তায় মইরা যাইতাছি। একটা খবর দিবেন না যে ফিরবেন না?’
গুণ হাসতে হাসতে বললেন, ‘তুই জানলি কেমনে আমি যে নাসরিনের বাসায়?’
গীতার উৎকণ্ঠিত মুখে প্রশান্তি এখন, ‘অসীমদা কইল যে দিদির বাসায় থাকতে পারেন।’
‘রিক্সা দিয়া আইছস না হাইট্যা?’ গুন জিজ্ঞেস করেন।
‘হাইট্যা কি এতদূর আইতে পারাম। রিক্সা লইছি।’
‘ভাড়া দিছস?’
‘না, রিক্সারে গেটের সামনে খাড়া কইরা থইয়া আইছি।’
‘তুই যে আইলি, তুই ইস্কুলে যাইতি না?’
‘হ যাইয়াম। চলেন বাড়িত চলেন। আমার ইস্কুলের দেরি অইয়া যাইব।’
নির্মলেন্দু গুণ চা নাস্তা খেয়ে গীতাকে নিয়ে চলে যান। গুণ তাঁর কাব্য সমগ্রের প্রথম পর্ব উৎসর্গ করেছেন কবি শামসুর রাহমানকে, দ্বিতীয় পর্ব উৎসর্গ করেছেন এই গীতাকে, গীতা গাণ্ডীবা দাসীকে। গীতা আজিমপুরের একটি ইশকুলে ঘণ্টা বাজাবার কাজ করে। এখন সে কারও বাড়ির কাজের মহিলা নয়। শরীরটি শক্ত সমর্থ, টান টান। মাথাটি উঁচু। গীতার ছোট বোনগুলোকে গীতা নিজের কাছে নিয়ে এসেছে, তাদেরও কোথাও কাজে নামিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে তার। গুণ আমাকে বলেছেন আমার বাড়িতে কোনও একটিকে তিনি পাঠাবেন কাজ করতে। কুলসুম বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে গীতার ছোট বোন বেবিকে নিয়ে এসেছিলাম বাড়ির কাজ করার জন্য। বেবি বেশিদিন থাকেনি। পরে একসময় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে শুরু করে। সুইয়ে সুতো ভরার কাজ। মাসে তিনশ টাকা মাইনে।
নির্মলেন্দু গুণের পরিবারের ঘনিষ্ঠ লোক এরাই। গুণের মুখে এদের গল্প অনেক শুনি। একবার গুণকে বলেছিলাম, তিনি কেন বস্তি ছেড়ে উঠে আসছেন না, কেন তিনি একটি ভাল জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে থাকছেন না। গুণ আমাকে বুঝিয়ে বলেন, ভাল জায়গা ওদের জন্য বস্তিই। ওখানেই ওরা আনন্দে থাকে। চেঁচিয়ে গালি গালাজ করে ইচ্ছে মত থাকা যায়। মধ্যবিত্ত ভাল এলাকায় এরকম বস্তিপনা প্রতিবেশিদের সহ্য হবে না। গীতা আর গীতার বোনদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বাড়িভাড়া নিতে গেলে প্রশ্নও উঠবে। বস্তিতে এসব প্রশ্ন কখনও ওঠে না। এ কথা ঠিকই, সমাজের কঠোর কঠোর নিয়মগুলো মধ্যবিত্ত শিক্ষিতরাই পালন করে, উচ্চবিত্ত আর নিম্নবিত্তই কোনও রীতি নীতির ধার ধারে না। এটা করলে ইজ্জত যাবে, ওটা করলে মান যাবে এসব মধ্যবিত্তের ব্যপার। নির্মলেন্দু গুণের অবাধ যাতায়াত সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। নিজে তিনি শ্রেণীহীন মানুষ। অনেকটা রাজহাঁসের মত, আজিমপুর বস্তির আবর্জনা তাঁর গায়ে লাগছে না, গুলশানের অট্টালিকার চাকচিক্য তাঁকে স্পর্শ করছে না।
নির্মলেন্দু গুণ কোনওদিন জুয়ো খেলায় জেতেননি। খেলায় বসা মানে, খেলায় হারা। তারপরও তিনি খেলতে যান জুয়ো। বলেছিলাম, ‘ধুর, বাদ দেন তো। কেন খেলেন এই সব? সময় নষ্ট। পয়সা নষ্ট।’
গুণ মলিন মুখে বলেন, ‘কি করব বল। না খেইলা তো উপায় নাই।’
‘উপায় নাই কেন?’
গুণ খেলার সঙ্গীদের দোষ দিয়ে বললেন, ‘আমি না খেললে আমারে ওরা হারামজাদা বইলা গাল দেয়।’
হারামজাদা গাল খেতে তিনি পছন্দ করেন না বলে জুয়ো খেলতে যান।
জীবন নিয়ে তিনি যত মজাই করুন না কেন, রাজনীতির ব্যপারে তিনি খুবই সিরিয়াস। তবে একানব্বই এর নির্বাচনে তিনি এ নিয়ে একটু মজা করেছিলেন। তাঁর খুব নির্বাচনে দাঁড়াবার শখ হল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যেহেতু তিনি আওয়ামি লীগের ঘোর সমর্থক, আওয়ামি লীগ থেকে তিনি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পাবেন। কিন্তু মনোনয়ন তাঁকে দেওয়া হল না। না দিলে কি হবে, নির্বাচন তিনি করতে চেয়েছেন, করবেন যে করেই হোক। কুমীর মার্কায় দাঁড়িয়ে গেলেন সতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। নৌকো নেই ভাগ্যে, কিন্তু কুমীর তো আছে। নেত্রকোনা ছেয়ে ফেললেন পোস্টারে, পুরোদমে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। কবিতা পড়ার কণ্ঠ স্লোগান দিতে দিতে বক্তৃতা করতে করতে ঘরে ঘরে গিয়ে ভোট চাইতে চাইতে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। গলায় কাগজের মালা পরে রিক্সায় দাঁড়িয়ে হাত দোলাতে দোলাতে পেছনে কুমীর মার্কার সমর্থক নিয়ে স্বতন্ত্র নেতা নির্মলেন্দু গুণ ঘুরে বেড়ালেন পুরো নেত্রকোণা। এতে অবশ্য তাঁর নির্বাচনের অভিজ্ঞতা হল অনেক, তবে ভোটে জেতা হয়নি। সাকুল্যে পাঁচটি ভোট পেয়েছিলেন।
শেখ মুজিবকে নিয়ে একমাত্র নির্মলেন্দু গুণই সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী কবিতা লিখেছেন। যে আওয়ামি লীগ নির্মলেন্দু গুণের কবিতা ব্যবহার করে যে কোনও উৎসবে অনুষ্ঠানে, সেই আওয়ামি লীগ অনেক অগাবগাগাগরুছাগলকে প্রার্থী করেছে, নির্মলেন্দু গুণকে করেনি। শেখ মুজিবকে নিয়ে যখন কেউ কোনও কথা বলতে সাহস পায়নি, লেখালেখি তো দূরের কথা, সেই সময় গুণই কাউকে পরোয়া না করে কবিতা লিখে গেছেন এবং প্রকাশ্য সভায় প্রথম তিনিই নির্ভয়ে সেসব কবিতা পড়েছেন। ‘মুজিব মানে আর কিছু না, মুজিব মানে মুক্তি, পিতার সাথে সন্তানের না লেখা প্রেম চুক্তি। মুজিব মানে আর কিছু না, মুজিব মানে শক্তি, উন্নত শির বীর বাঙালির চিরকালের ভক্তি।’ গুণের কবিতা আওয়ামি লীগের খুব বড় সম্পদ। রেসকোর্সের ময়দানে একাত্তর সালের সাতই মার্চের ভাষণকে তিনি কবিতা আর মুজিবকে কবি বলে উল্লেখ করে লিখেছেন স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে আমাদের হল কবিতাটি। বিএনপি যখন দাবি করছে জিয়াউর রহমান ছিলেন স্বাধীনতার ঘোষক, তখন একাত্তরে মুজিবের মহান ভূমিকাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে আওয়ামি লীগ, আপাদমস্তক মুজিবভক্ত কবি নির্মলেন্দু গুণকে নিজেদের সভা সমাবেশে ডেকে মুজিবকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলো পড়িয়ে বেশ গর্বিত মুজিব কন্যা হাসিনা। গুণ তাঁর ভরাট কণ্ঠে পিন পতন নিস্তব্ধতার মধ্যে পড়েন, সমবেত সকলের মত আমিও গোলাপফুল খুব ভালবাসি/রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপের একটি গোলাপ /গতকাল কানে কানে আমাকে বলেছে/ আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি/আমি তার কথা বলতে এসেছি। /সমকাল পার হয়ে যেতে সদ্যফোঁটা একটি পলাশ/ গতকাল কানে কানে আমাকে বলেছে /আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি/ আমি তার কথা বলতে এসেছি।/ শাহবাগ এভিন্যূর ঘুর্ণায়িত জলের ঝর্ণাটি গতকাল/ আর্তস্বরে আমাকে বলেছে /আমি যেন কবিতায় মুজিবের কথা বলি/আমি তার কথা বলতে এসেছি।/ শহীদ মিনার থেকে খসে পড়া একটি রক্তাক্ত ইট/ গতকাল কানে কানে আমাকে বলেছে/ আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি/ আমি তার কথা বলতে এসেছি।/ সমবেত সকলের মত আমারও স্বপ্নের প্রতি পক্ষপাত আছে /ভালবাসা আছে –গতকাল রাতে দেখা একটি সাহসী স্বপ্ন/ গতকাল কানে কানে আমাকে বলেছে আমি যেন/ কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি/ আমি তার কথা বলতে এসেছি।/এই বটমূলে সমবেত মানুষগুলো সাক্ষী থাকুক/ না ফোটা কৃষ্ণচূড়ার অপ্রস্তুত প্রাণের এই গোপন মঞ্জুরিগুলি কান পেতে শুনুক/ বিষণ্ন বসন্তের এই কালো কোকিলটি জেনে যাক/ আমার পায়ের তলার পূন্য মাটি ছুঁয়ে/ আমি আজ সেই গোলাপের কথা রাখলাম/ সেই পলাশের কথা রাখলাম/ আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি,/আমি আমার ভালবাসার কথা বলতে এসেছিলাম।
আওয়ামি লীগের সঙ্গে তার পরও নির্মলেন্দু গুণ সম্পর্ক নষ্ট করেননি। হাসিনার সঙ্গে তাঁর আগের মতই ভাল সম্পর্ক। হাসিনা বিরোধী দলের নেষনী হিসেবে মিন্টোরোডের সরকারি বাসভবনে ওঠার পর যেহেতু সরকারি দল থেকে বিশাল করে ইফতার পার্টির আয়োজন করেছে, তিনিও করেছেন আয়োজন। হাসিনার ইফতার পার্টিতে যাবার আমন্ত্রণ জোটে আমার। আমি আর গুণ ভরা পেটে হাসিনার দাওয়াত খেতে যাই। গুণের পকেটে একটি ডোভ ক্রিমের কৌটো, আমেরিকা থেকে আনা হাসিনার জন্য একটি উপহার। আমার খালি হাত, খালি পকেট, ভরা শুধু চোখ দুটো, রাজনৈতিক ইফতার দেখার কৌতূহলে। মিন্টো রোডের বাড়ির মাঠে বিশাল ত্রিপলের তলে চেয়ার টেবিল বসানো। মাইকে কোরান তেলোয়াত হচ্ছে। রোজদার আওয়ামী নেতারা সাইরেন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিসমিল্লাহ বলে পানি মুখে দিয়ে রোজা ভাঙছেন। হাসিনা ঘোমটা মাথায় টেবিলে টেবিলে গিয়ে অতিথিদের সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। আজ তিনি খবর করে দিচ্ছেন যে আওয়ামী লীগও বিএনপি বা জামাতে ইসলামীর মত ধর্মভীরু দল। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির এই মিশ্রণ আমি দেখতে থাকি বড় বেদনার্ত বড় ভীত চোখে।
ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল এ দেশে, এখন সিদ্ধ। যে জামাতে ইসলামির খুনীরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গর্তে লুকিয়েছিল, তারাই এখন এ দেশের সংসদের মহামান্য সদস্য। কি ভীষণ পাল্টো গেছে দিন! জামাতে ইসলামি আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছোতে পারত না, যদি না তারা বিএনপি আর আওয়ামী লীগের আশকারা পেত। একাত্তরের গণহত্যাকারী গোলাম আযম বাংলাদেশে ফিরে জামাতে ইসলামির আমীর হয়ে বসেছেন। ঘাতক দালালরা এখন মাথা উঁচু করে এ দেশে চলাফেরা করে। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কিছু মানুষ, জাহানারা ইমাম এই কমিটিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একাত্তরের দিনগুলি নামে তিনি একটি স্মৃতিকথা লিখেছেন, ভয়াবহ সেই দিনগুলির বর্ণনা আছে বইয়ে। যুদ্ধে কী করে তিনি তাঁর স্বামী আর পুত্রকে হারিয়েছেন লিখেছেন। জাহানারা ইমামের বাড়িতে একদিন খোকা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। জাহানারা ইমাম তখন গোলাম আযমের শাস্তি হওয়ার পক্ষে জনগণের সই যোগাড় করছিলেন। আমাকেও দিয়েছিলেন সই যোগাড়ের দায়িত্ব। নির্মূল কমিটির উদ্যোগে সোহরোওয়ার্দী উদ্যানে যেদিন গণআদালত ডেকে গোলাম আযমের বিচার করা হয়, সেদিন হাজার হাজার দর্শকের মিছিলে আমিও ছিলাম। গণআদালতে গোলাম আযমের ফাঁসির রায় হল। কিন্তু ফাঁসি কে দেবে তাঁকে! সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে গণআদালত পণ্ড করতে। পুলিশ এসে স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনের জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে, মাইক খুলে নিয়েছে, মঞ্চ ভেঙে ফেলেছে। গোলাম আযমকেও জেলে ভরা হয়েছে, নেহাতই লোক দেখানো জেল। পাকিস্তানি পাসপোর্টে এ দেশে ঢুকে ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও কেন থাকছেন— এই তুচ্ছ অপরাধের জন্য তাঁকে জেলে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু একাত্তরের যুদ্ধের সময় যে তিনি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার পক্ষ হয়ে হাজার হাজার বাঙালিকে খুন করেছেন তাঁর সেই অপরাধ নিয়ে সরকারের মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না। আমার আশঙ্কা হয় পরিস্থিতি শান্ত হলে গোলাম আযমকে জেল থেকে আবার না মুক্তি দেওয়া হয়, গোলাম আযম এ দেশের নাগরিকত্বের জন্য যে আবেদন করেছেন, সেই নাগরিকত্ব না আবার তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয়। এই দেশটি দেখতে তখন কেমন হবে! আদৌ কি বাসযোগ্য হবে! ধর্ম যেরকম প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠছে রাজনীতির, আমার আশঙ্কা হয় ধীরে ধীরে জামাতে ইসলামির হাতেই না চলে যায় রাষ্ট্রক্ষমতা একদিন!
শান্তিবাগে কুলসুম ফিরে এসেছে। পালিয়ে সে বেশিদূর যেতে পারেনি। যদিও তার ইচ্ছে ছিল ময়মনসিংহে তাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যাওয়ার, ওখানে তার মাকে আর বোনকে নিয়ে জীবন যাপন করার, সেই স্বপ্নটি সফল হয়নি কুলসুমের। শান্তিবাগেই এক বাড়িতে সে কিছুদিন কাজ করেছে, ওখানে অশান্তি এমন বেশি যে ও বাড়ি থেকে পালিয়ে আবার আমার বাড়িতেই এসে থেমেছে। কুলসুম তেরো চৌদ্দ বছরের কিশোরী। এ বয়সেই পাঁচবেলা নামাজ পড়ে, সবগুলো রোজা রাখে, মাথা থেকে ওড়না সরতে দেয় না। পীর বাড়িতে অনেকদিন কাজ করেছে, ওখান থেকেই মাথায় আবর্জনা ভরে এনেছে সে। একদিন কুলসুমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘এই যে নামাজ রোজা করস, কী লাভ!’
কুলসুম ঘর মুছছিল, বালতির পানিতে নোংরা ত্যানা ধুয়ে চিপে আবার মেঝেয় ফেলে মুছতে মুছতে বলে, ‘বেহেস্তে যাইতে পারব।’
‘বেহেস্তে কী আছে?’ আমি জিজ্ঞেস করি।
কুলসুম ঘর মোছা থামিয়ে মিষ্টি করে হাসে। চোখের তারাদুটো ঝিলমিল করছে ওর। বলল, ‘বেহেস্তে মাছের কলিজা খাইতে দিব আল্লাহ।’
আমি বলি, ‘মাছের কলিজা? তর মাছের কলিজা খাইতে ইচ্ছ! করতাছে? যা, তরে মাছের কলিজা খাওয়াবো। শান্তিনগর বাজার থেইকা কালকেই আমি মাছের কলিজা কিন্যা আনব।’ কুলসুমের নাক কুঁচকে ওঠে, ঠোঁট বেঁকে থাকে, কপালে ভুরুতে ভাঁজ পড়ে বাজারের মাছের কলিজার কথা শুনে।
‘মাছের কলিজা তো তর খাইলেই হইল। এহন নামাজ রোজা বাদ দিয়া দে। মাথার কাপড় ফালা। এই গরমের মধ্যে মাথায় যে কাপড় দিয়া রাখস, আরও তো গরম লাগে। মাছের কলিজা..’
কুলসুম ওড়নাটিকে টেনে মাথার ওপর আরও বেশি করে এনে বলে, ‘দুনিয়ার মাছের কলিজা তিতা, বেহেস্তের মাছের কলিজা মিষ্টি।’
আমি হো হো করে হেসে উঠি। আমার হাসির দিকে কুলসুম বিরক্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে বেরিয়ে যায়। আমাকে পাগল ভাবে নয়ত বোকার হদ্দ ভাবে।
১৪. পেষণ
পূর্বাভাস পত্রিকা আপিসে হামলা হয়েছে, রাতের অন্ধকারে এক দল দুর্বৃত্ত আপিসে ঢুকে জিনিসপত্র ভেঙে চুরে সব তছনছ করে গেছে। এর কারণ আমার লেখা। আমার লেখা পছন্দ হচ্ছে না অনেকের। ধর্মীয় মৌলবাদীরা পূর্বাভাস পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলাও করেছে। একদিন গিয়ে দেখে আসি আপিসের দুরবস্থা। খুব মন খারাপ হয়ে যায়। এত মন খারাপ হয় যে লেখালেখি ছেড়ে দেবার কথা ভাবি। ডাক্তারি করছি, হাসপাতালে চাকরি করে বাড়তি সময় যা থাকে সে সময়ে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে কাজ করলে দিব্যি সংসার চালিয়ে নিতে পারব। সিদ্ধান্তটি নিয়ে আমি লেখা বন্ধ করে দিই। কিন্তু মোজাম্মেল বাবু তা মানবে না, পূর্বাভাসের জন্য লেখা সে চেয়েই যাচ্ছে। জরুরি তলব করল, দেখা করতে গেলে সেই এক কথা, ‘আপা আপনি লেখা বন্ধ করলে চলবে নাকি? লেখেন। আজকেই একটা লেখা দেন।’
হুমায়ুন আজাদ ফোন করেছেন তখন। তিনিও কলাম লেখেন পূর্বাভাসে। বাবু তাঁকে জানাল যে আমি লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছি। শুনে তিনি কথা বলতে চাইলেন আমার সঙ্গে, আমার সিদ্ধান্ত শুনে বললেন, ‘ লেখা ছাড়বেন না, আপনার লেখা খুব ভাল হচ্ছে। লেখা চালিয়ে যান, কিছু দুষ্ট লোক কি করল কি বলল তা নিয়ে মোটেও ভাববেন না।’
হুমায়ুন আজাদের মত আরও অনেকেই উপদেশ দেন, পত্রিকায় লেখা আবার শুরু করার উপদেশ। কেউ কেউ বলেন, ধর্ম সম্পর্কে অত কড়া কথা না লিখলে কোনও অসুবিধে হবে না।
আমি লিখতে শুরু করি, কারণ না লিখে পারি না বলে। কয়েকদিন না লিখে দেখি ভেতরে কথা জমে জমে পাহাড় হয়ে আছে। হুমায়ুন আজাদ পূর্বাভাসে নতুন ধরণের কলাম লেখা শুরু করেছেন, রাজনীতি সমাজ ইত্যাদি নিয়ে কৌতুক করা হুমায়ুন আজাদ এখন নারী নিয়ে লিখছেন, না, আগে যেমন তিনি নারীর বদনাম গেয়ে প্রবচন রচনা করেছিলেন, তেমন নয়, এবারের লেখা নারীর গুণ গেয়ে। হুমায়ুন আজাদের লেখা আমার তখনও পড়া হয়নি, কিন্তু যেদিন নির্মলেন্দু গুণ আমাকে বললেন ‘হুমায়ুন আজাদ জনপ্রিয় হতে চাইছেন, তাই তোমার লেখা নকল করে তিনিও লিখতে শুরু করেছেন,’ পড়ে ঠিকই দেখি যে যে কথা আমি অনেক আগেই বলেছি, সে কথাগুলোই তিনি লিখছেন নতুন করে, তিনি বহু বই ঘেঁটে উদাহরণ দিচ্ছেন, আমি কোনও বই না ঘেঁটে মনে যা ছিল তাই লিখেছি, এই যা তফাৎ।
বইমেলা শুরু হচ্ছে। এবারের মেলায় আমার কয়েকটি বই প্রকাশ পাচ্ছে। কবিতার বই, কলামের বই, উপন্যাস। ফজলুল আলম আমার কবিতার ইংরেজিতে অনুবাদ করে লাইট আপ অ্যাট মিডনাইট নামের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন। বইটি কে প্রকাশ করবে? এগিয়ে এলেন বিদ্যাপ্রকাশ। ফজলুল আলমের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার আরমানিটোলার বাড়িতে। ও বাড়িতেই আমাকে অবাক করে দিয়ে ফরিদুর রেজা সাগর তাঁর লন্ডনপ্রবাসী কাকাকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সাগরের বহুমুখী প্রতিভা। লেখিকা রাবেয়া খাতুনের গুণধর পুত্র তিনি। তিনি নিজেও সাহিত্যিক। বাচ্চাদের জন্য অনেকগুলো বই লিখেছেন। টেলিভিশনে বাচ্চাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ব্যবসাতেও সাফল্য তাঁর অনেক। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক। আজকের কাগজ, খবরের কাগজেরও আধখানা মালিক হয়েছেন। এমনিতে সাগরকে সাহিত্যের আড্ডায় মোটেও দেখা যায় না। তিনি থাকেন তাঁর ব্যবসা নিয়ে। স্টেডিয়ামের কাছে খাবার দাবার নামে খুব ভাল একটি রেস্তোরাঁ আছে তাঁর। পাঁচবেলা নামাজ পড়েন সাগর, শান্তিনগরে তাঁর বিরাট আপিসে একটি নামাজের ঘর করে নিয়েছেন। রোজার মাসে তিরিশটা রোজা রাখেন। নিভৃতে লেখেন। নিভৃতে ছাপেন। ব্যস্ত লোক। ব্যস্ত লোকই তাঁর দুলাল কাককুর আবদারে আমার সঙ্গে দেখা করাতে এনেছেন, খুঁজে খুঁজে আরমানিটোলায়। দেশে বেড়াতে এসে ফজলুল আলমের প্রথম কথাই ছিল আমার সঙ্গে পরিচিত হবেন। লন্ডনে বসেকাগজে আমার কলাম পড়েই তাঁর এই আবেগ। একবার আমার সঙ্গে দেখা না করে তিনি যাবেন না। ফজলুল আলম আমুদে লোক। স্পষ্টভাষী, সৎ, কোদালকে যার তার সামনে কোদাল বলতে দ্বিধা করেন না, এতে লোকের মন খারাপ হলে হোক। লোকটি দেখতে বালুর বস্তার মত, কানে কম শোনেন, চেঁচিয়ে কথা বলেন, অল্প কিছুতেই ঠা ঠা করে হাসেন। সাগরের সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল, তাঁর বাড়িতে অনেকদিন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছি, কেবল নেমন্তন্ন খেতে নয়, মন ভাল না থাকলে অনেকদিনই চলে গিয়েছি সাগরের বাড়িতে। সাগর না থাক, সাগরের স্ত্রী আছেন, তাঁর মা আছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। সাগরের মা রাবেয়া খাতুন আমাকে ডেকে সাহিত্য নিয়ে কথা বলেছেন, লেখালেখির প্রসঙ্গ এলে আমি মনের কথাটি বলে দিই সবাইকে যে কি করে লিখতে হয় আমি জানি না, যা লিখি আদৌ কোনও লেখা হয় বলে মনে হয় না, কি করে উপন্যাস লিখতে হয় তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, মৃদুভাষী রাবেয়া খাতুন আমাকে বলেছেন খুব কনসেনট্রেশন লাগে। এই জিনিসটিই যে আমার নেই আমি নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করেছি। তাঁর বাবা কি করে তাঁর মাকে ছেড়ে চলে গেছেন, কি করে সংসারটির দৈন্যদশা তিনি ঘুচিয়েছেন, কি করে তিনি একটি নির্যাতিতা মেয়েকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে বিয়ে করেছেন, সাগর আমাকে সব কথা খুব বন্ধু মনে করে বলেন। সাগরদের বাড়ির সবাইকে আমার খুব আপন মনে হয়। এই আপন পরিবারটির আপন লোক ফজলুল আলমও আমার খুব আপন হয়ে ওঠেন। ফজলুল আলম নিজে লন্ডনের বাংলা পত্রিকায় লেখালেখি করছেন অনেকদিন থেকে, খবরের কাগজেও লিখেছেন কলাম। আমিই তাঁকে একদিন বলি লেখাগুলো জড়ো করে একটি বই বের করতে। তিনি খুব উৎসাহে লেখা জড়ো করলেন। নাম দিলেন বইয়ের। এবার আমার দায়িত্ব প্রকাশক খোঁজা। আমার তো এক খোকাই আছেন অনুরোধ করার। তিনি, তত নাম নেই লেখক হিসেবে, এমন লোকের বই ছাপবেন কেন! আমার অনুরোধে ঢেঁকিটি গিললেন শেষ অবদি। বইয়ের পঈচ্ছদ আমি নিজে এঁকে দিলাম। ফজলুল আলমের খুশি দেখে কে! তিনি লন্ডনে যাওয়া পিছিয়ে দিলেন অথবা গিয়েও আবার ফিরে এলেন দেশে। এবারের বই মেলায় তাঁর বই থাকছে, তিনি কি না থেকে পারেন!
বই মেলা শুরু হয়ে গেল। পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বইমেলা। বইমেলার মাসটি লেখকদের মাস। লেখকেরা সারা বছর এই মাসটির অপেক্ষায় বসে থাকেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে রফিক সালাম বরকত এ মাসে প্রাণ দিয়েছিলেন। এ মাসটি বাংলা ভাষার মাস। বাংলা সাহিত্যের, বাংলা গানের উৎসব। মেলায় সাহিত্যিক বিষয় নিয়ে ধুম আড্ডা হচ্ছে। বিরানব্বই সালের ফেব্রুয়ারিতে আমার আনন্দও কম নয়। আমার একাধিক বই মেলায় এসেছে, তার ওপর বিক্রি হচ্ছে খুব, মেলাতেই প্রথম মুদ্রণ শেষ, দ্বিতীয় মুদ্রণের জন্য প্রকাশক ছাপাখানায় দৌড়োচ্ছেন। খবর বেরোচ্ছে, ‘হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন আর তসলিমা নাসরিন এই তিনজনের বই বিক্রির শীর্ষ তালিকায়।’ ইমদাদুল হক মিলন অনেক আগে থেকেই জনপ্রিয় লেখক। হুমায়ুন আহমেদ তাঁর নন্দিত নরকে লিখে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়ে চলে গিয়েছিলেন আমেরিকায়। ওখান থেকে দেশে ফিরে নতুন করে লেখালেখি শুরু করলেন। মাত্র বছর কয় আগেও দেখেছি বুকের ওপর দুহাত আড়াআড়ি রেখে একা একা হাঁটছেন মেলায়। হুমায়ুন আহমেদের সঙ্গে তখনই আলাপ। তাঁকে যেদিন আমি বর্ণনা করেছি তাঁর লেখা আমরা ভাই বোনেরা কি করে পড়তাম বাড়িতে, একজন সশব্দে পড়েছে, বাকিরা শুনেছে —শুনে তিনি খুব আনন্দ পেলেন। বললেন তাঁর বাড়িতেও ওভাবে বই পড়া হত। ময়মনসিংহে মোহনগঞ্জে বড় হয়েছেন হুমায়ুন আহমেদ, কথা বলায় ময়মনসিংহের টান আছে। এরপর থেকে মেলায় এসে তিনি আমাকে খুঁজে বের করে পুরোনো দিনের গল্প বলতেন। আমাকে ডাকতেন কবি বলে। কবির খবর কি আজ? কবি চলেন চা খাই। গল্প বলতে তিনি এত চমৎকার পারেন যে তার শ্রোতা হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা যায়। আমার খুব ভাল লাগত হুমায়ুনের আহমেদের গল্প শুনতে, তিনি খুব চেনা জীবনের গল্প বলেন। নিজের কথাই বলেন, নিজের ভাই বোনের কথা বলেন, পাশের বাড়ির লোকের কথা বলেন, মফস্বলের এইসব মধ্যবিত্ত মানুষের সুখ দুঃখ নিয়ে কথা শুনে মনে হত চোখের সামনে দেখছি তাদের, যেন আমারই আত্মীয় স্বজন তারা। টেলিভিশনে যখন তাঁর নাটক সবে প্রচার হতে শুরু হল তিনি নাটকের রাতে বন্ধু বান্ধবদের ডাকতেন একসঙ্গে বসে নাটক দেখার জন্য। হুমায়ুন আহমেদ তখন আজিমপুরের ছোট একটি অ্যাপার্টমেণ্টে থাকতেন। সেখানে আমি আর নির্মলেন্দু গুণ তাঁর একা নাটকটি দেখেছিলাম। নাটকটি প্রচার হওয়ার আগে হুমায়ুন আহমেদ অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন ঘরময়। তাঁর নাকি এরকমই হয় নাটকের আগে, খুব টেনশন হয়। অতি সাধারণ জীবন যাপন হুমায়ুন আহমেদের। আমেরিকায় অনেক বছর থেকে এসেছেন, তারপরও মনে হয় গ্রাম থেকে মাত্র শহরে এসে উঠেছেন। পাড়ার হিমু ভাইএর মত তিনি, উদাসীন, পড়ুয়া, জমিয়ে গপ্প করা, কারও সাতে নেই পাঁচে নেই, তরতর করে একা একা সিঁড়ি পেরোচ্ছেন। হিমু ভাইএর মত সত্যি সত্যি অনেক সিঁড়ি চোখের সামনে পার হয়ে গেলেন হুমায়ুন আহমেদ। এখন তাঁর সঙ্গে খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় না আর, কারণ তাঁর জনপ্রিয়তা। টেলিভিশনের নাটক তাঁকে এমন গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা দিয়েছে যে এখন তিনি আর মেলায় একা একা হাঁটার লেখক নন। যতক্ষণ মেলায় থাকেন, ততক্ষণই তিনি অদৃশ্য হয়ে থাকে অটোগ্রাফ শিকারিরা আড়ালে। আমি যখন কলাম লিখছি কাগজে তখন একবার হুমায়ুন আহমেদ আমাকে ডেকে বলেছিলেন যে কলামগুলো পড়লে তাঁর তিন কন্যার জন্য খুব দুশ্চিন্তা হয় তাঁর, মেয়েদের জীবন যে ভয়াবহ রকমের নিরাপত্তাহীন তা তিনি অনুভব করতে পারছেন আগের চেয়ে বেশি করে। হুমায়ুন আহমেদের লেখার আমি শুরু থেকেই ভক্ত। অনেকে বলে তাঁর লেখা কালজয়ী নয়, উপন্যাসগুলো হালকা, চরিত্রগুলো পলকা, যে যাই বলুক আমার মনে হয় তিনি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছেন তাঁর লেখা দিয়ে। এই কাজটি সহজ কাজ নয়। তাঁর তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের চোখ জানে পাঠকরা কি চায়, তিনি পাঠকের চাওয়া মেটাচ্ছেন। যারা কখনও বই পড়েনি বা পড়তে চায়নি, তারা আর কারও বই না পড়লেও তাঁর বই পড়ে। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ, তিনি প্রচুর পাঠক তৈরি করছেন।
বইমেলায় বিদ্যাপ্রকাশের স্টলে প্রতি বিকেলে আমাকে বসার জন্য অনুরোধ করেন খোকা। অন্য প্রকাশকরাও তাদের স্টলে আমাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও বসার আবদার করেন। কোথাও আমার বসে থাকতে ইচ্ছে করে না দীর্ঘক্ষণ। ইচ্ছে করে মেলায় হাঁটতে, মানুষ দেখতে, লেখক বন্ধুদের সঙ্গে মেলার দোকানে গিয়ে চা খেতে খেতে আড্ডা দিতে। কিন্তু খোকার অনুরোধে আমাকে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হয় তাঁর স্টলে। ক্রেতারা বই কিনে সই নিতে চায়, সই দিতে হয় বসে বসে। অনেকে বই হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দাম দেখে চলে যায়, পকেটে পয়সা নেই বলে কিনতে পারে না। ইচ্ছে করে বিনে পয়সায় তাদের দিয়ে দিই বই। কয়েকজনকে এমন দিই, খোকা ‘করছেন কি করছেন কিঞ্চ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলে বলি, ‘এটা আমার সৌজন্য কপির পাওনা বই থেকে দিলাম।’ টাকার সঙ্গে বইএর সম্পর্কটি বড় অস্বস্তিতে ফেলে আমাকে। খোকা বলেন, ‘এত দিলদরিয়া হলে চলবে নাকি! আপনি এখন প্রফেশনাল লেখক।’
‘কি যে বলছেন! আমি ভাই ডাক্তারি করি, সেটা আমার প্রফেশন। লেখা আমার হবি।’ খোকা তা মানেন না। বই বেচেই তিনি সংসার চালান। স্টলে খোকা আছেন বউ, শালি শালা সব নিয়ে। উত্তেজিত ফজলুল আলম বারবার স্টলে এসে খবর নিচ্ছেন তাঁর বই আদৌ কেউ কিনেছে কী না। পরিচিত কাউকে পেলে ধরে ধরে নিজের বই দেখাতে নিয়ে আসছেন। হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে এলেন একবার। হুমায়ুন আজাদ লাইট আপ এ্যাট মিডনাইট বইটি উল্টোপাল্টো দেখে বললেন, সেই কবিতাটি নেই, ‘সাত সকালে খড় কুড়োতে গিয়ে আমার ঝুড়ি উপচে গেছে ফুলে!’ ফজলুল আলম বললেন, না নেই।’ হুমায়ুন আজাদ বললেন, ‘তা থাকবে কেন! ভাল কবিতা থাকবে কেন!’
আমি হেসে বলি, ‘আমার কবিতা বুঝি ভাল!’
আজাদ আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, ‘নিশ্চয়ই। আপনার অনেক কবিতাই আমার ভাল লাগে।’
আমি বলি, ‘তবে যে সেদিন পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিলেন, আমি নাকি কবিই নই, আমার কলাম আপনি পড়েন না, কারণ কলামগুলো বালক বালিকারা পড়তে পারে!’ হুমায়ুন আজাদ কোনও উত্তর না দিয়ে বিদেয় নিলেন। হাসিটি তখন তেমন আর বিμছুর মত লেগে ছিল না মুখে। এই হুমায়ুন আজাদই খবরের কাগজে আমার লেখা জনপ্রিয় হওয়ায় ক্ষেপে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন। এই হুমায়ুন আজাদই পূর্বাভাস আপিসে ফোনে আমাকে বলেছেন আমার কলাম তাঁর ভাল লাগে। হুমায়ুন আজাদকে আমার নিতান্তই বালক বলে মনে হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক, অত্যন্ত জ্ঞানী লোক, খুব ভাল লেখেন, তাঁর কবিতা, তাঁর গদ্য অত্যন্ত উন্নতমানের। কিন্তু এত গুণের অধিকারী হয়েও তিনি উদ্ভট উদ্ভট সব কাণ্ড করেন। অনেকে বলে এসব নিতান্তই তাঁর স্টান্টবাজি, লোকের নজরে পড়তে চান, তাই এসব করেন। তিনি গালাগাল দিয়ে বেড়ান সব লেখকদের, কবিদের। কিছু চেলা চামুণ্ডা নিয়ে মেলায় হাঁটেন, চেলারা উঠতে বসতে তাঁর প্রশংসা করেন। তিনি বেজায় রকম উপভোগ করেন এসব।
ফজলুল আলম লন্ডনি কায়দায় চলা লোক, ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেন না এই মেলায়। আমার লেজ হয়ে থাকতে চান, আমি বসলে তিনি বসেন, দাঁড়ালে তিনি দাঁড়ান। আমি যেদিকে যাই, তিনি সেদিকে যান। আমি স্টলে এসে বসব, তিনিও স্টলে এসে বসবেন, আমি চা খেতে যাবো, তিনিও চা খেতে যাবেন। দেখে আমার রাগ হয়, বলি, ‘দুলাল কাককু, আপনি কি একা ঘুরে বেড়াতে পারেন না!’ ফজলুল আলম মন খারাপ করে আমার সঙ্গ ছাড়েন। মেলায় একা একা হাঁটেন অগত্যা। এদিকে তাঁর বইও বিক্রি হচ্ছে না যে মনে একটু সুখ পাবেন। মেলায় কোনও বন্ধু বা চেনা কাউকে খুঁজে পান না যার সঙ্গে কথা বলবেন। আমারও সময় নেই তাঁকে সময় দেওয়ার। কানে কম শোনেন বলে যে কোনও কথার উত্তর চেঁচিয়ে দেন, সেটি আরও বিরক্তিকর। বইমেলা শুরু হওয়ার আগে ফজলুল আলম আমাকে একবার নিয়ে গিয়েছিলেন এনায়েতুল্লাহ খানের বাড়ির পার্টিতে। আমার মোটেও ভাল লাগেনি বাড়িটিতে। কাউকেও আন্তরিক মনে হয়নি। ধনী স্বামীদের সঙ্গে সুন্দরী স্ত্রীরা ভয়াবহ রকম সেজে পার্টিতে এসে মদ খাচ্ছিলেন আর নিজেদের পরিচয় দিচ্ছিলেন মিসেস শাহাবুদ্দিন মিসেস আলম বলে বলে। কোনও মেয়েকেই দেখিনি যার নিজের কোনও পরিচয় আছে। আমার কাছে অদ্ভুত লাগছিল সবকিছু। টাকা পয়সা, ধন দৌলত, বাড়ি গাড়ি, ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল না। জমজমাট পার্টি পেছনে ফেলে বেরিয়ে এসেছিলাম। এরপর ফজলুল আলমের ওপর আমার আরও একবার রাগ হয়েছিল। আমি ময়মনসিংহে যাবো বলে তিনি সাগরের গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন আমাকে নিয়ে কিন্তু এত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন যে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। লণ্ডনে যে গতিতে তিনি গাড়ি চালান, একই গতি বাংলাদেশেও দিয়ে বসে আছেন। চিৎকার করেছি, যেন তিনি ধীরে চালান গাড়ি। কিন্তু ধীরে কি করে গাড়ি চালাতে হয় তা তিনি জানেন না, এককালে জানলেও ভুলে গেছেন। তিনি ভ্যাবাচাক্যা খেয়ে যাচ্ছেন, ধাককা ট্রাকের সঙ্গে লাগে, গরু গাড়ির সঙ্গে, রিক্সার সঙ্গে, বাসের সঙ্গে, এমনকী মানুষের সঙ্গেও লাগে লাগে।
সেদিন সতেরোই ফেব্রুয়ারির সন্ধেবেলা। মেলায় একটি চাপা উত্তেজনার গন্ধ পাওয়া যায়। উত্তেজনা কেন, কিসের জন্য, আমার জানা হয় না কিছু। বিশাল একটি ব্যানার নিয়ে একটি মিছিল বিদ্যাপ্রকাশের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। মেলার মধ্যে ব্যানার নিয়ে মিছিল! এ আবার কেমন! এমন তো দেখিনি আগে কোনওদিন! কি সেই মিছিল কেন সেই মিছিল প্রশ্ন করে কারও কাছ থেকে উত্তর পাওয়া যায় না। হঠাৎ দেখি খোকা টেবিল থেকে আমার বইগুলো দ্রুত তুলে ফেলছেন, বইয়ের তাক থেকে খোকার শালা আমার বই নামিয়ে নিচ্ছেন। তখনই হঠাৎ মুহম্মদ নূরুল হুদা আর রফিক আজাদ আমাকে বের করে নিলেন স্টল থেকে। আমাকে নিয়ে বাংলা একাডেমির মূল দালানের ভেতর ঢুকে গেলেন। একেবারে মহাপরিচালকের ঘরে। ঘটনা কি! ঘটনা যা জানা গেল, তা হল, আমার বিরুদ্ধে মেলায় মিছিল বের হয়েছে। তসলিমা নাসরিন পেষণ কমিটি এই মিছিলটি করছে, যৌন-লেখিকা তসলিমাকে পিষে মারার জন্য এই মিছিল। মেলার বইয়ের স্টলগুলোয় কমিটির লোকেরা হুমকি দিয়ে এসেছে আমার বই যেন না রাখা হয় কোথাও। রাখলে ওরা স্টল ভেঙে ফেলবে নয়তো পুড়িয়ে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার বই যে স্টলগুলোয় ছিল, সরিয়ে ফেলা হল। আমি স্তম্ভিত বসে থাকি। ঘরে আরও লেখক বসা ছিলেন। ফজলুল আলমও উঠে এসেছিলেন আমার পেছন পেছন। আশঙ্কায় তাঁর মুখ চোখ সব গোল গোল হয়ে আছে। মহাপরিচালকের ঘরে এই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। মিছিল কেন হয়েছে, কারা করেছে, মেলার অস্থিরতা কি করে বন্ধ করা যায়। ব্যানারে কী লেখা এই নিয়ে ফিসফিস চলছে লেখকদের মধ্যে। মহাপরিচালক হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন, ‘কেন এই মিছিল হচ্ছে? আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি ওদের?’
‘তা তো আমি জানি না কি অভিযোগ।’ আমি বলি।
মহাপরিচালক গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, ‘খুব অশ্লীল কথা লেখা আছে ব্যানারে। কি মনে হয় আপনার, কেন এসব করছে ওরা?’
‘সম্ভবত আমার লেখার কারণে।’
‘লেখে তো অনেকেই। এই যে এখানে যত লেখক আছেন, সকলেই বই লেখেন। তাঁদের বিরুদ্ধে তো মেলায় মিছিল হয় না। আপনার বিরুদ্ধে হয় কেন?’
ফজলুল আলমের কণ্ঠস্বর উঁচুতে উঠল, ‘হয় কেন মানে? উনি কি করে জানবেন হয় কেন! যারা হওয়ায় তারা জানে, কেন। আর তসলিমা নাসরিনের লেখা সকলে গ্রহণ করতে যাবে কেন! তাঁর লেখা তো আর সবার মত আপোসের লেখা না!’
গুঞ্জন ওঠে লেখকদের মধ্যে। তবে কি তিনি তাঁদের বলছেন আপোস করে লেখেন তাঁরা। গুঞ্জন থামিয়ে মহাপরিচালক ভুরু কুঁচকে চাইলেন আমার দিকে, আমাকে বললেন, ‘মেয়ে হয়ে আপনি পুরুষের মত লিখতে যান কেন? সে কারণেই তো ঝামেলা হচ্ছে।’
আমি ঝটিতে উত্তর দিই, ‘আমি পুরুষের মত লিখব কেন! আমি আমার মত করে লিখি।’ বসে থাকা লেখকরা একটু নড়ে চড়ে বসেন।
‘সবাইকে সব কিছু মানায় না। তা কি বুঝতে পারেন না?’ মহাপরিচালকের ঠোঁটের কোণে একটি হাসি ঝিকমিক করে। লেখকদের নিঃশ্বাসের টানে কিছু ঝিকমিক তাঁদের ঠোঁটের কোণেও আশ্রয় নেয়।
‘আপনার লেখা আমি পড়েছি। কোনও মেয়ে কি আপনি যে ভাষায় লেখেন, সে ভাষায় লেখে?’
আমি চুপ।
‘না, লেখে না।’
মহাপরিচালকের মন্তব্যে লেখকদের মাথাও নড়ে, না লেখে না।
আমার চোয়াল শক্ত হচ্ছে।
‘আপনার লেখা খুব অশ্লীল।’
এবার দাঁতে দাঁত চেপে মেয়ে বলে, ‘আমার লেখা — কারও কাছে তা অশ্লীল মনে হয়, কারও কাছে মনে হয় না।’
মুহম্মদ নূরুল হুদা বাইরে গিয়ে মাইকে ঘোষণা দিয়ে আসেন যে মেলার মধ্যে কোনও মিছিল যেন না হয়, এতে মেলার পরিবেশ নষ্ট হয়। কারও যদি কোনও অভিযোগ থেকে থাকে তবে যেন তা মেলা কমিটির সদস্যদের জানানো হয়। শান্ত হতে বলেন তিনি মিছিলের জনতাকে।
আগুন আগুন বলে একটি রব ওঠে মেলায়। ঘরে বসা লোকগুলোর কেউ কেউ জানালার দিকে ছুটে যান ঘটনা দেখতে। বই পোড়ানো হচ্ছে মেলার মাঠে। আমার বই মিছিলের লোকেরা যে যেখানে পেয়েছে মাঠের মাঝখানে জড়ো করে পুড়িয়ে দিয়েছে।
খোকা দাঁড়িয়ে আছেন মহাপরিচালক হারুন উর রশীদের ঘরের বারান্দায়। আমি উঠে যাই খোকার কাছে। খোকা ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে আছেন, ঘামছেন তিনি। চোয়াল খোকারও শক্ত হয়ে আছে।
‘কারা এই মিছিল করছে খোকা ভাই? জানেন কিছু?’
খোকা মাথা নাড়লেন। তিনি জানেন না।
মহাপরিচালক মেলাকমিটির সদস্য বাংলা একাডেমির উপপরিচালকদের সঙ্গে আলোচনা করে আমাকে জানালেন, ‘আপনি মেলায় না এলে ভাল হয়।’
‘এ কেমন কথা, কেন আমি আসব না?’
ফজলুল আলম বলে ওঠেন, ‘কেন তিনি আসবেন না? তাঁর কি দোষ?’
‘উনি এলে মেলায় গণ্ডগোল হয়, তাই তিনি আসবেন না।’
জানিয়ে দিলেন, মেলায় যদি আমার ওপর কোনও আক্রমণ হয়, সেই দায়িত্ব মেলা কমিটি নিতে পারবে না। সুতরাং আমার নিরাপত্তার জন্য বইমেলায় আমার না আসাই ভাল। আমার জন্য মেলার পরিবেশ নষ্ট হোক, মেলা পণ্ড হয়ে যাক, তা তাঁরা চান না।
ফজলুল আলম চোখ কপালে তুলে বলেন, ‘আপনারা মেলা কমিটির লোক, আপনারা তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।’
ফজলুল আলমের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকান মহাপরিচালক। চোখের ভুরুতে প্রশ্ন, লোকটি কে এখানে চিৎকার করছে! একে তো চিনি না!
কিছু ছেলে আমার বিরুদ্ধে মিছিল করছে বলে আমার মেলায় আসা বন্ধ হবে কেন! অনেকে তো আমার লেখা পছন্দ করে, তারা ..
আমার কোনও যুক্তিই মহাপরিচালক মেনে নেন না। মীমাংসা শেষ অবদি কিছুই হয় না। মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যে স্থির থাকেন। তাঁর পরামর্শ আমার আর মেলায় আসা উচিত নয়। যেহেতু আমি মেয়ে হয়ে পুরুষের মত লিখি, যেহেতু আমি অশ্লীল লেখা লিখি, যেহেতু আমার লেখা আদৌ কোনও ভাল লেখা নয়, সেহেতু আমার বিরুদ্ধে মেলায় মিছিল বের হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, আমাকে লোকে পেষণ করতে চাইবে, এও অবাক করা কোনও ব্যপার নয়। সুতরাং আমি যেন মেলা থেকে দূরে থাকি, এ যত না আমার নিরাপত্তার জন্য, তার চেয়ে বেশি মেলার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার জন্য।
পুলিশের ভ্যানে তুলে দিয়ে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
মেলা জমজমাট। আমার মেলায় যাওয়া নিষেধ। লেখা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ আমি দেখেছি। গতবারের মেলায় এক দল ছেলে, বয়স উনিশ কুড়ি হবে, হাতে আমার একটি কবিতার বই নিয়ে আমার কাছে এসে বিপরীত খেলা নামের একটি কবিতা দেখিয়ে বলেছিল, ‘আমি দশ টাকায় বিক্রি হতে চাই। আমাকে কেনেন।’ প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি মজা করছে। কিন্তু এরপরই যখন কড়া স্বরে চোখ পাকিয়ে বলল যে এক্ষুনি তাকে কিনতেই হবে আমার। আমি থতমত খেয়ে ঢোক গিলে মৃদু স্বরে বলেছি, ‘এটি কবিতা। সত্যিকার কেনার জন্য নয়।’ বলে কিছুটা পিছনে সরে এসেছি। খোকা লক্ষ করেছেন ব্যপারটি। তিনি স্টল থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছেলেদের ডেকে বললেন, ‘বিক্রি হতে চাও ঠিক আছে, বিক্রি হলে কবিতায় আর যে সব শর্ত আছে, তা মানতে পারবে তো! পুরো কবিতা পড়ে তারপর বিক্রি হতে এসো।’
‘আমার এখন দশ পাঁচ টাকায় ছেলে কিনতে ইচ্ছে করে। ছেলে কিনে ছেলেকে তছনছ করে বুকে পিঠে লাথি কষে বলব, যাশশালা। ছেলে কিনে ছেলের কুঞ্চিত অণ্ডকোষে লাথি কষে বলে উঠবো, যাশশালা।.. ‘
কবিতাটি লিখেছিলাম রমনা পার্কের সামনে সন্ধের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা দরিদ্র মেয়েদের ভদ্রলোকরা রিক্সা উঠিয়ে নিচ্ছেন দেখতে দেখতে। কোথায় নিয়ে যায় ওদের! কী করে ওদের নিয়ে! বড় কৌতূহল হয়। একদিন হেঁটে যাচ্ছিল!ম রমনার পাশ দিয়ে, ভাঙা আয়না সামনে নিয়ে তেলহীন শুকনো চুলে চিরুনি আর ধুলো বসা মুখে পাউডার লাগাতে থাকা মেয়েদের সামনে থেমে জিজ্ঞেস করেছি, ‘কেন সাজতাছেন এইখানে বইসা?’
আমার প্রশ্নের দিকে কেউ তাকায় না।
আবারও প্রশ্ন করলে একজন বলে, ‘পেটের ধান্দা করি বইন। পেটের ধান্দা।’
উসকো খুসকো চুল, রোদে পোড়া ত্বক, গালে বাহুতে কাটা দাগ, কারও চোখ ফুলে আছে, কারও কপাল। কপাল ফুলে লাল হয়ে আছে একটি অল্প বয়সী মেয়ে রেলিংএ হেলান দিয়ে উদাস দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করি, ‘কপালে কি হইছে?’
আমার দিকে একবার দৃষ্টি ফেলে সরিয়ে নেয় মেয়েটি। আমি যেন এক উপদ্রব ছাড়া কিছু নই। আমাকে তার প্রয়োজন নেই। কপালে কি হয়েছে তা বলার প্রয়োজন সে বোধ করে না। তবু আমি দাঁড়িয়ে থাকি। লু হাওয়ায় শুকনো চুল উড়ে মুখের ঘামে সেঁটে থাকে। সেই চুলও মেয়েটি সরিয়ে দেয় না। ইচ্ছে করে নিজে হাতে সরিয়ে দিই চুল, ইচ্ছে করে বাড়িতে নিয়ে মেয়েটিকে গোসল করিয়ে ভাল খাইয়ে দাইয়ে বিছানা দিই ঘুমোবার। চোখে ঘুম মেয়েটির। কত রাত বোধহয় ঘুমোয় না। মেয়েটি হঠাৎ বলে, কপালের দোষে কপাল পুড়ে, কপাল ফাটে, কপাল দিয়া রক্ত ঝরে।’
ধ ধু চোখদুটো এবার আমার দিকে ফিরিয়ে বলে, ‘বেডারা মারছে গো, বেডারা মারছে। আমি জিজ্ঞেস করি, ‘মারছে কেন?’
‘মারার শখ হইছে, মারছে।’
‘কত টাকা পান? কত টাকা দেয় তারা?’
‘দশটেকা। পাঁচটেকা। কোনওদিন দুই টেকা। কোনওদিন কোনও টেকা পয়সা দেয় না। লাত্থি দেয়, লাত্থি।’
মেয়েটি তেতো একটি হাসি মুখে নিয়ে সরে যায় আমার সামনে থেকে। বাকি মেয়েগুলোও তাদের প্রসাধনসামগ্রী নিয়ে দ্রুত উধাও। পুলিশ আসছে। পুলিশও তো পুরুষ। পুলিশও কি ভোগ করেনা এদের! করে। না করলেও অন্তত টাকা তো নেয়, এদের দশ পাঁচ টাকা থেকেও ভাগ নিতে দ্বিধা করে না। শর্ত মার দেবে না, জেলে পুরবে না। যে লোকেরা এদের দরদাম করে রিক্সায় উঠিয়ে নেয়, তাদের কি পুলিশ কখনও জেলে পুরতে চেয়েছে! চায়নি। তাদের কি কেউ মন্দ বলে? না, বলে না। নিজেকেই প্রশ্ন করতে করতে নিজেকেই উত্তর দিতে দিতে আমি হাঁটি। বুকের ভেতর কষ্টের পাথর নিয়ে হাঁটি।
বইমেলায় যাওয়া আমার জন্য নিষেধ, এ খবরটি খোকাকে ভীষণ রকম হতাশ করে। তিনি বই-ব্যবসা ভুলে যান, ভুলে যান বই ছাপা, প্রতিদিনকার টাকা পয়সার হিসেব নেওয়ার কাজ। এমনকী বইমেলায় যাওয়া বন্ধ করে দেন। তিনি দিন রাত ব্যস্ত ‘তসলিমা নাসরিন পেষণ কমিটিঞ্চর নাড়ি নক্ষত্র জানতে। কে এরা, কি করে, কি উদ্দেশ্য এদের, কোনও দল করে কি না, করলে কোন দল ইত্যাদি খবর নেন। কমিটির সভাপতি বিএনপির কর্মী এই খবর পেয়ে খোকা তাঁর খালাতো না কি মামাতো ভাইকে ধরে যেহেতু ভাইটি বিএনপির ছোটখাটো এক নেতা, সভাপতিটির সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে চান। সমঝোতা কেবল মুখের কথায় হয় না, অর্থকড়ি ঢালতে হয়। খোকার কত টাকা গচ্চা যায় তা আমার জানা হয় না। কিন্তু টাকা খেয়েও যখন প্রতিপক্ষের ক্রোধ কমে না, তখন মুখোমুখি কথা বলার ব্যবস্থা করেন খোকা। প্রতিপক্ষ নেতা বনাম আমি। খোকার মুহুর্মুহু অনুরোধে আমি শেষ পর্যন্ত রাজি হই। খোকা আমাকে পই পই করে বলে দেন যে আমাকে উত্তেজিত হলে চলবে না, সভাপতি যা প্রশ্ন করবে তার উত্তর যেন আমি মাথা ঠাণ্ডা করে দিই। প্রশ্নোত্তরের বৈঠকটি হবে খোকার বাড়িতে। আমার ওপর বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের গুরুণ্ডাদেশ দেখে ফজলুল আলমের চোখ মুখ সেই যে গোল হয়ে ছিল, গোল হয়েই আছে। এই গোপন খবরটি শুনে যে আমি যাচ্ছি পেষণ কমিটির নেতার সঙ্গে দেখা করতে, গোঁ ধরলেন তিনিও যাবেন। তাঁর আশঙ্কা আমার ওপর আবার আক্রমণ করার চেষ্টা করবে নেতা। আমার বিপদ দেখলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে বাঁচাবেন। আমি তাঁকে কিছুতেই সঙ্গে নেব না, কিন্তু তিনি যাবেনই। তিনি গেলেন। কিন্তু খোকা রাজি হন না বৈঠকে ফজলুল আলমের উপস্থিতি। নেতা শুধু আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, যদি তৃতীয় কারও ঘরে থাকতে হয়, বড় জোর খোকা থাকতে পারেন, কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর খোকাকে দিলে চলবে না, দিতে হবে আমাকে। খোকা ঠাণ্ডা মাথার লোক, তিনি অবস্থা বেগতিক দেখলে সামাল দেবার চেষ্টা করবেন। ফজলুল আলমের গরম মাথাকে তিনি পাশের ঘরে একটি পাখার তলে রেখে দিলেন। এসময় ঠাণ্ডা মাথা দরকার, গরম মাথা যে কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে, খোকার ধারণা। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমাকে পিষে মারার জন্য দল গঠন করেছে, সেই ছাত্রনেতার মুখোমুখি বসি। নেতা দশাসই চেহারার কিছু নয়। নেতার মুখে মোচ, ব্রণ, ঘৃণা সব স্থির হয়ে আছে। আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়, চোখে আমাকে পিষে মারার তৃষ্ণা থিকথিক করে। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ শোনার পালা আমার। ছেলেটি, কী নাম তার, হাফিজ বা হারুন বা হামিদ বা হাসান কিছু একটা হবে, বলল, ‘আপনি আমাদের মা বোনদের সর্বনাশ করছেন।’
‘কি রকম সর্বনাশ করছি?’
‘কি রকম সর্বনাশ করছেন জানেন না?’
‘আমি তো জানি, আমি মেয়েদের পক্ষে লিখি, আমি তাদের সর্বনাশ করতে যাবো কেন?’
‘তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন। সংসার ভেঙে তারা যেন বার হইয়া যায়।’
‘এরকম কথা আমি কোথাও তো বলি নাই।’
‘আপনার বালিকার গোল্লাছুট কবিতায় বলছেন, পৃথিবীর সকল বয়ষ্ক বালিকা দিই গোল্লা থেকে ছুট।’
হামিদ বা হাসান আমার কবিতার বই খুলে কবিতাটি দেখায়।
‘পড়েন, কবিতাটা আবার পড়েন। কী মনে করে এই কবিতা লিখেছেন, বলেন আমাকে।’
কণ্ঠস্বরের হুকুম এবং হুমকি দুটোই কান থেকে প্রাণে এসে বিষমাখা তীরের মত বেঁধে।
‘আমরা বালিকারা যে খেলাটি খেলব বলে পৃথিবীতে বিকেল নামত
সে খেলার নাম গোল্লাছুট
…. আমার আবার ইচ্ছে করে খেলি
এখনো মাঝে মধ্যে আঁকুপাঁকু করে পায়ের আঙুল
ধুলোয় ডুবতে চায় গোপন গোড়ালি
ইচ্ছে করে, যাই
পৃথিবীর সকল বয়ষ্ক বালিকা দিই গোল্লা থেকে ছুট।’
জবানবন্দি। যেন আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি, যাহা বলিব সত্য বলিব বলে আমাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। দিতে হবে, কারণ এই নেতাটি যতই হালকা পাতলা হোক, তাকে দু ঘা মেরে হয়ত বসিয়ে দেওয়া যাবে, তাকে দেখে শক্তিহীন মনে হলেও সে কিন্তু অসীম শক্তি ধারণ করে। সে একটি দল গঠন করার শক্তি রাখে, তারও চেয়ে বড় কথা তার দলবল নিয়ে আমাকে পিষে মারার শক্তি রাখে।
‘সকল বয়ষ্ক বালিকাকে গোল্লা থেকে ছুটে যেতে প্রেরণা দিচ্ছেন। আমাদের মা বোনেরা যেন সংসার ছেড়ে বের হইয়া যায়। আপনি এই সমাজের কত বড় ক্ষতি করছেন, তা জানেন?’
‘এটি গোল্লাছুট খেলা নিয়ে কবিতা। মেয়েরা যারা একসময় গোল্লাছুট খেলত ছোটবেলায়, বড় হয়ে গেলে তারা আর সেই খেলাটা খেলতে পারে না। ভেতরে ইচ্ছ!টা তো থাকে। আমি আমার ইচ্ছ!র কথা বলেছি।’
‘উহুঁ ।’ হাফিজ বা হাবিব মাথা নাড়ে।
‘আপনি এইখানে সকল বয়ষ্ক বালিকার কথা বলছেন। আপনার নিজের কথা কেবল বলেন নাই।’
‘সব মেয়েরই এমন ইচ্ছ! হয়। সবাই তো পেছনে ফেরে, শৈশবে ফিরতে চায়। চায় না কি? চায় তো। আমি যখন নিজের কথা বলি, একই সঙ্গে অনুভব করি যে এ অন্য মেয়েদেরও কথা। এই কবিতায় মেয়েদের ইচ্ছ!র কথা বলেছি….’
‘সব মেয়ের তো এমন ইচ্ছ! করে না..’
‘অনেকের করে।’
‘না অনেকের করে না। বলেন যে আপনার করে।’
আমি ঠিক বুঝে পাই না কি বলব।
হাবিব বা হারুন এবার তীক্ষ্ম চোখে আমার চোখে তাকিয়ে বলে, ‘গোল্লা বলতে তো আপনি স্বামী সন্তাান নিয়ে মেয়েরা যে সংসারটা করছে, তা বোঝাতে চেয়েছেন।’
আড়চোখে খোকাকে দেখি। খোকার চোখে আকুলতা, ‘ একবার আপনাকে আমি নেবই বইমেলায়, আপনি বলুন যে আপনি সংসার বোঝাননি, কেবল খেলাই বুঝিয়েছেন।’ আমি এই আকুলতার সামনে প্রায় বলতে যাওয়া ‘একভাবে ভাবতে গেলে এটি সংসারও হয়, সমাজের নিয়মের যে জাল পাতা মেয়েদের জন্য, সেটিও হয়’ আর বলি না। আমার মুখ খোলার আগেই হাসান বা হাফিজ বলে, ‘অন্য মেয়েদের ইচ্ছ!র কথা কি করে জানেন?’ হাতের কাছে বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলি, ‘সেটা আমার মনে হয়েছে।’
‘কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলেন লেখার আগে যে তারা গোল্লা থেকে ছুটতে চায় কি না? নাকি আপনি আপনাকে দিয়ে বিচার করেন সবাইকে?’ নেতার চোখ থেকে কিছু একটা বেরোয়। সেই কিছু একটার ঝাঁঝ আমার মুখটি তুলতে দিচ্ছে না।
বইটি টেবিলে রেখে দিয়ে বলি, ‘না, তা করি না।’
‘আপনার মনে হয়েছে অন্য মেয়েদের ইচ্ছ!টা কী। কিন্তু আপনি সঠিক জানেন না।’
এবার নেতার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আমি বলি, ‘আমার ইচ্ছে, আমার মনে হওয়ার কথা তো আমি লিখব আমার কবিতায়। এটা কি দোষের কিছু?’
‘নিশ্চয়ই দোষের।’
‘কী দোষের?’
খোকা খুব আলতো স্বরে বলেন, ‘লেখা তো লেখকেরা যা ভাল মনে করেন, তাই লেখেন। সবাই তো আর সব লেখকের সব লেখাকে ভাল মনে করে না। তাদের সব বক্তব্যই তো সব পাঠক মেনে নেয় না। তবে আমার মনে হয় উনি বোঝাতে চেয়েছেন গোল্লাছুট খেলার কথা। লেখাটা পড়লে অনেকে ভুল বুঝতে পারে।’
খোকার বক্তব্যে মাথা নেড়ে আমি বলি, ‘হ্যাঁ, অনেকেই ভুল বোঝে। তা ঠিক। যেমন ধরেন ওই বিপরীত খেলা কবিতাটা। ওই কবিতায় কি আমি সত্যিই ছেলে কিনতে চেয়েছি? ওই কবিতাটি ছিল একটি প্রতিবাদ!’
‘এই কথাটাই আপনি ওকে বুঝিয়ে বলেন না কেন! খোকা বলেন আমাকে।’
‘আমি তো বোঝাচ্ছিই। বলতে চাইছি যে এক লেখাকে অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা করে। লেখকের এক রকম ব্যাখ্যা থাকে, পাঠকের হয়ত আরেক রকম।’
ছাত্রনেতাটি আমাকে পিষে মারার জন্য বড় একটি দল বানিয়েছে। হাতের কাছে পেলে পুরো মেলার মানুষ যেন দেখে আমাকে ন্যাংটো করে পায়ের তলায় পিষবে, তেমন কথা ছিল। এই নেতাকে আমি নতুন করে বোঝাবো কী! আমার লেখার কিছুই না বুঝে সে দল বানায়নি। তার আশঙ্কা আমি সমাজটাকে নষ্ট করছি। মা বোনের মাথা বিগড়ে দিচ্ছি। এই বিশ্বাস কেবল এই হাসান বা হামিদের নয়, আরও অনেকের। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ঠিক বুঝতে পারি না, আমার গোল্লাছুটের সরল ব্যাখ্যাটি আদৌ সে মেনে নিয়েছে কী না। খোকার সঙ্গে আবার চোখাচোখি হয়। চোখের এবারের ভাষাটি আমার পক্ষে পড়া সম্ভব হয় না।
নেতা এবার জয় বাংলা কবিতা নিয়ে প্রশ্ন করল। ‘জয় বাংলা কবিতাটা কেন লিখেছেন?
আমার সহজ উত্তর, ‘জয় বাংলায় বিশ্বাস করি বলে।’
‘এই কবিতায় তো আপনি যারা জয় বাংলায় বিশ্বাস করে না, সেই দুর্ভাগাদের মৃত্যু চাইছেন। আমি তো জয় বাংলা মানি না। আপনি আমাকে দুর্ভাগা বলবেন কেন? যারা মানে না, তাদের সম্পর্কে বাজে কথা বলবেন কেন?’
‘আপনি কি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না?’
‘বিশ্বাস করব না কেন? অবশ্যই করি।’
আমার গলার স্বরে সত্যিই ফুটে উঠতে থাকে উত্তেজনা, ‘যদি করেন বিশ্বাস তাহলে জয় বাংলায় বিশ্বাস না করার তো কোনও কারণ নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে কী স্লোগান আমরা সবাই দিয়েছিলাম? সবাই বলেছে জয় বাংলা। সবাই জয় বাংলার গান গেয়েছে।’ নেতার ক্রুদ্ধ মুখ থেকে চোখ খোকার দিকে ফিরিয়ে বলি, ‘কী খোকা ভাই, একাত্তরে জয় বাংলা বলেন নাই? একমাত্র রাজাকার আলবদররাই জয় বাংলা বলে নাই। আমি তাদেরই দুর্ভাগা বলছি।’
‘জয় বাংলা আওয়ামি লীগের স্লোগান।’ নেতা কঠিন কণ্ঠে বলে। নাকের পাটা ফুলে উঠছে তার।
‘জয় বাংলা আওয়ামি লীগের হবে কেন? এটা সবার। জয় বাংলা মানে বাংলার বিজয়, জয় বাংলা মানে স্বাধীন বাংলা। মুক্তিযোদ্ধারা, যারা কোনওদিন আওয়ামি লীগ করে নাই, তারা কি জয় বাংলা বলত না সবসময়ই? এই জয় বাংলা বলেই তো তারা প্রেরণা পেত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার।’
খোকা একগাল হেসে বলেন, ‘ওর ওইসময় হয়ত জন্মই হয় নাই। আপনার জন্ম বোধহয় যুদ্ধের পরে। ঠিক না?’
নেতাটির মাথা না বোধক নড়তে নিয়েও নড়ে না।
খোকা আমাকে বলেন, ‘আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন! ওরা তো মুক্তিযুদ্ধে কি হয়েছিল, তা জানে না। জানলেও হয়ত মনে নাই। জয় বাংলা, এটা তো সত্যি যে আওয়ামি লীগ এটাকে নিজেদের স্লোগান করে নিয়েছে। আওয়ামি লীগের তো কোনও রাইট নাই জয় বাংলা..’
আমি মাথা নেড়ে বলি, ‘আওয়ামি লীগ একে নিজের সম্পত্তি মনে করলেই তো হবে না। জয় বাংলা কোনও দলের সম্পত্তি না। আমি তো জয় বাংলা সেই একাত্তর থেকে বলে আসছি। আমি তো কোনওদিন আওয়ামি লীগে নাম লেখাই নাই। আমি তো নিরপেক্ষ মানুষ। রাজনীতি করি না। আওয়ামি লীগের অনেক কিছুই আমার পছন্দ না।’ প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে তখনও সন্তুষ্ট না হওয়া হাসান বা হাবিব বা হাফিজ বা হামিদের সঙ্গে খোকার আরেক দফা বৈঠক হয়। খোকা না চাইলেও মুখে মধুর হাসি টেনে সব জুলুম সহ্য করছেন কারণ তিনি যে করেই হোক অন্তত একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে আমাকে নিয়ে যেতে চান মেলায়। বইমেলায় বই বিক্রি তাঁর জন্য বড় কোনও বিষয় নয়, আমার মেলায় যাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর কাছে এখন সবকিছুর চাইতে জরুরি। কিন্তু এভাবে কি স্বস্তি মেলে? সারাক্ষণই একটি উৎকণ্ঠা কি পায়ে পায়ে হাঁটে না! পেষণ কমিটির সভাপতি কথা দিয়েছে যে আক্রমণ আপাতত তার দল করছে না, কিন্তু ভবিষ্যতে আমি যেন খুব সাবধানে লিখি, যদি অশ্লীল লেখা লিখি, যদি মা বোনের ক্ষতি করার জন্য লিখি, যদি সমাজের অনিষ্ট করার জন্য লিখি, তবে পেষণ কমিটির কর্মকাণ্ড অনেকদূর এগোবে। বলেছে দলের একজন, কিন্তু দলের বাকিরা কি এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে যে আপাতত আমার ওপর হামলা করবে না! খোকা আমাকে জানান যে নিয়েছে। কিন্তু তারপরও খোকা জানি না কোত্থেকে কিছু পেশীবহুল লোক যোগাড় করলেন, যাদের কাজ আমাকে মেলায় নিয়ে যাওয়া আর মেলা শেষ হলে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। অচেনা পেশী পরিবেষ্টিত হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন মেলায় যাই বটে আমি, আগের সেই স্বতস্ফূর্ত আনন্দ জোটে না কিছুতে তবে খোকার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে থাকে। কোনও লেখক তো এগিয়ে আসেনি কোনও সাহায্য করতে, মেলা কমিটি মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, এ সময় খোকা এই মীমাংসাটি না করলে আমাকে এক ঘোর হতাশার মধ্যে ঘরে বসে থাকতে হত। যে দুটো দিন মেলায় গিয়েছি, বিদ্যাপ্রকাশের স্টলেই বসে ছিলাম। মেলার মাঠে হাঁটাহাঁটি বা চায়ের স্টলে গিয়ে চা খাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হলেও যেতে পারিনি। স্টলেও বেশিক্ষণ বসা হয়নি, ঘণ্টা দুঘণ্টা পর বাড়ি ফিরতে হয়েছে। তবে আমি যে যে করেই হোক গিয়েছি মেলায়, সেটিই ছিল বড় ঘটনা। যদিও আশঙ্কা নামের কুৎসিত একটি জিনিসকে কোনও আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিতে পারিনি, যদিও খোকার চোখ সারাক্ষণই অস্থির ছিল উদ্বেগে তবু বিজয়ের প্রশান্তি অল্প হলেও কিছু ছিল তাঁর মনে। ফজলুল আলম উৎকণ্ঠা এবং উচ্ছঅ!স দুটো নিয়েই নিরাপদ একটি দূরত্বে হাঁটাহাঁটি করেন। বইমেলা কমিটির লোকেরা আমাকে ভ্রু কুঁচকে দেখেছেন। জ্বলজ্যান্ত উপদ্রুবটিকে দেখতে তাঁদের ভাল লাগেনি। আমার মত আস্ত একটি সমস্যা মেলায় উপস্থিত হলে কী না কী অঘটন ঘটে কে জানে! মেলায় যদি জ্বালাও পোড়াও শুরু হয়ে যায়, তবে! তার চেয়ে একা আমাকে কোথাও নিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলে মেলাটা অন্তত বাঁচে। মেলার স্টলগুলোয় আমার বই নেই। বেশির ভাগই ছিনিয়ে নিয়েছে পেষণ কমিটির লোকেরা। বেশির ভাগই পুড়িয়ে দিয়েছে। কোনও কোনও স্টলে বই আছে, সেসব বই লুকিয়ে রাখা হয়েছে টেবিলের তলায়।
প্রতি বছরের মত বাংলা একাডেমি কবিতা পড়ার অনুষ্ঠান করছে। আগের বছরের অনুষ্ঠানগুলোয় কবিতা পড়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, এবার আমি আমন্ত্রিত নই।
আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার, পিষে মারার ষড়যন্ত্র যেমন একদিকে চলছে, অন্যদিকে আবার অনেক পাঠকই একবার আমাকে চোখের দেখা দেখতে মেলায় আসেন। কাছে এসে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বলেন, ‘আপনাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।’ কেউ বলতে বলতে যে আমার লেখা যেন লেখা নয়, সত্যিকার জীবন, কেঁদে ফেলে। কেউ বলে, ‘যে কথা আমি সবসময় বলতে চেয়েছি, পারিনি, আপনি বলছেন।’ কোনও মা আসেন মেয়ে নিয়ে, মেয়েকে পাঠান আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিতে। কেউ কেউ সিলেট চট্টগ্রাম রাজশাহী বগুড়া এসব দূর দূর শহর থেকে ঢাকার বইমেলায় আসেন একটি উদ্দেশ্য নিয়েই, কাছ থেকে যদি সম্ভব না হয়, দূর থেকে হলেও আমাকে একটিবার দেখে স্বপ্ন পুরণ করবেন।
আমার জন্য মানুষের ভালবাসা এবং ঘৃণা দুটোই আমাকে কাঁদায়।
১৫. আনন্দধারা
শুভাকাঙ্খীদের আনাগোনা বাড়ে শান্তিবাগের বাড়িতে। অনেকের মত রাকা আর আলতাফ ভক্ত হিসেবে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে অচিরে বন্ধু বনে যান। দুজনেই শখের রবীন্দ্রসঙ্গীত গান, আলতাফ নিজে কবিও। দুজনে বেশি বয়সে বিয়ে করে বাচ্চাকাচ্চাহীন জীবন যাপন করছেন। আগে বিয়ে হয়েছিল দুজনের, আলাদা আলাদা করে ছেলে মেয়ে আছে, ছমাসে কি বছরে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া তাঁদের বিশেষ কোনও কর্তব্য নেই। দশটা পাঁচটা চাকরি করেও অখণ্ড সময় পড়ে থাকে হাতে, বিশেষ করে সন্ধ্যেগুলো। সন্ধ্যেগুলোয় প্রায়ই আমার বাড়িতে চলে আসেন দুজন। গানে কবিতায় মুখরিত শান্তিবাগের বাড়িটিতে বসেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঘোরে একদিন বলি ‘চলুন শান্তিনিকেতনে বসন্তউৎসবে যাই।’ জীবনে কখনও শান্তিনিকেতন যাননি, অথচ রবীন্দ্রঅন্ত প্রাণ, খুশিতে লাফিয়ে ওঠেন রাকা আর আলতাফ। শান্তিবাগে বসেই শান্তিনিকেতনের জন্য আবেগ আমাদের উথলে ওঠে। এবার আর টাকা ধার করতে হয় না, প্রকাশকদের কল্যাণে পকেটে আমার যথেষ্ট টাকা। দুদিনের মধ্যেই রাকা আর আলতাফ টাকা যত খরচ হওয়ার কথা, তার চেয়ে দু হাজার বেশি পকেটে নিয়ে, সুটকেস গুছিয়ে তৈরি। দলের নেতা হলে দায়িত্ব অনেক। বেলাল চৌধুরীকে দিয়ে ভারতের ভিসা করিয়ে নিই তিনটি পাসপোর্টে। বেলাল চৌধুরী ভারতীয় দূতাবাসে ভারত বিচিত্রা পত্রিকাটি সম্পাদনার কাজ করেন। ভারত বিচিত্রায় আমার বেশ কিছু কবিতা তিনি ছেপেছেন। দেখা হলেই লেখা চান। দেখা প্রায়ই হয়, আরমানিটোলায় থাকা কালীন মাঝে মাঝে যখন করার কিছু থাকত না, তাঁর আপিসে গিয়ে গল্প শুনে সময় কেটেছে আমার। শান্তিবাগে অশান্তির সময়গুলোতেও অনেক সময় গিয়েছি ভারত বিচিত্রায়। বেলাল চৌধুরী আড্ডা দিতে পছন্দ করেন। ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প আছে তাঁর, পছন্দের কোনও শ্রোতা পেলে ঝুড়ি উপুড় করেন। পুরোনো আমলের সাহিত্য-জগতের কথা, কলকাতার সাহিত্যরথীদের ছোট খাটো ব্যক্তিগত গল্প খুব রসিয়ে মজিয়ে পরিবেশন করেন। সুস্বাদু গল্প সব। দীর্ঘকাল কলকাতা ছিলেন বলে কলকাতার সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর বেশ বন্ধুত্ব। কলকাতার কে কেমন, কে পাগল, কে ছাপল, কে উদার, কে উদাস জানতে জানতে , কলকাতার এ গলি ও গলির নানারকম গল্প শুনতে শুনতে মনে মনে কতবার যে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছি! বেলাল চৌধুরী কবিতা লেখেন কিন্তু তাঁর কবিতার চেয়ে বেশি ভাল লাগে তাঁর কথা। যে কোনও আড্ডা জমিয়ে তোলার অসম্ভব ক্ষমতা রাখেন তিনি। খুব একাকী মানুষ বেলাল চৌধুরী। খুব প্রাণখোলা। খুব আন্তরিক। খুব উদাসীন। খুব কবি। তিনি আমার দাদা- দাদা-বন্ধু হয়ে গেছেন অল্প কদিনের মধ্যেই। তিনিই একদিন আমাকে বলেছিলেন গিরিন্দ্রশেখর বসুর লাল কালো বইটির কথা। বাচ্চাদের জন্য এমন চমৎকার বই বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। দুঃখ করে বলেছেন যে বইটি এখন কোথাও আর পাওয়া যায় না, কোনও প্রকাশকই বইটির পুনর্মুদ্রণ করছে না। লাল কালোর গল্প শুনে বইটি পড়ার ইচ্ছে জাগে। বেলাল চৌধুরীর কাছেই একটি জীর্ণ পুরোনো পোকা খাওয়া লাল কালো বইটি পাতা উল্টো উল্টো দেখি। একদিন বইটি বাড়ি নিয়ে এসে পড়ে মুগ্ধ হয়ে বইটির পূনর্মুদ্রণের সংকল্প করি। মুদ্রণ ব্যপারটির জন্য খোকার শরণাপন্ন হই। খোকা আমার অনুরোধ রাখেন। তিনি লাল কালো বইটি ছাপার কাজে হাত দেন। আমি নিজে প্রুফ দেখে দিই। বেলাল চৌধুরীকে দিয়ে একটি ভূমিকা লিখিয়ে নিই। আজ দেবেন কাল দেবেন বলে তিনি দীর্ঘ সময় পার করেছিলেন ভূমিকাটি লিখতে। ভেতরে পিঁপড়ের রঙিন ছবিগুলো দেখে খোকা বলেছিলেন, ‘লেখাগুলো গেলেই তো চলবে, ছবির কি দরকার আছে?’ আমি বলেছি, ‘আছে, বাচ্চাদের বইতে ছবি থাকবে না, এ কেমন কথা? লেখা পড়ার চেয়ে বাচ্চারা তো বেশি পড়ে ছবি!’ খোকা ছবিসহ হুবুহু লাল কালো বইটি ছেপে দিলেন। একটি কাজের কাজ বটে। কাজটি করে আমার বেশ আনন্দ হয়, নিজের বই বেরোলে যেমন আনন্দ হয়, তেমন আনন্দ। নাহ, নিজের বই বেরোনোর আনন্দর চেয়ে বেশি এ আনন্দ। নিজের বই বেরোলে উচাটন মন আমার আনন্দকে নাশ করে ফেলে। বই হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতা উল্টো খুঁজতে থাকি ভুল। পাতায় পাতায় বাক্যের ভুল আর শব্দের ভুল গুনতে বসি, সংখ্যার পরিমাণ যত বাড়ে, তত আমার মন খারাপ বাড়ে। মন খারাপ বাড়লে আমার দ্বারা আর যাই হোক লেখালেখি যে হবে না এ ব্যপারে মোটামোটি নিশ্চিত হই।
শান্তিনিকেতনের বসন্তউৎসবে যাচ্ছি শুনে বেলাল চৌধুরী নিজের দেখা বসন্ত উৎসবের সুখদ বর্ণনা করলেন। বর্ণনা শেষে আমাকে বললেন একটি লাল কালো যেন শ্রীপান্থর জন্য নিয়ে যাই। শ্রীপান্থ আনন্দবাজারের কলকাতার কড়চায় বইটির একটি খবর দিয়ে দেবেন। লেখক শ্রীপান্থর নাম ঠিকানা বলে দিলেন। নাম নিখিল সরকার। শ্রীপান্থ তাঁর ছদ্মনাম। ঠিকানা আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট। শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা নামে একটি বইয়ের দোকান আছে, দোকানের মালিক ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গেও দেখা করতে বললেন। ইন্দ্রনাথের মত মানুষ নাকি পৃথিবীতে আর হয় না। শ্রীপান্থকে লাল কালো দেওয়া আর ইন্দ্রনাথের মত অসাধারণ মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, বেলাল চৌধুরীর দুটো আদেশ বা অনুরোধ আমি রক্ষা করব বলে কথা দিই।
তিনজনের দলটি মহানন্দে কলকাতা পৌঁছোই। প্রথমেই আমি সৌমিত্র মিত্রর খোঁজ করি পশ্চিমবঙ্গ তথ্যকেন্দ্রে। শাহরিয়ার একবার বলেছিল সৌমিত্র মিত্র হলেন কলকাতার ঈশ্বর। যে কোনও জটিল কাজই তিনি মুহূর্তে সরল করে দিতে পারেন। সৌমিত্র মিত্রই আমাদের বাসস্থান ঠিক করে দিলেন। কিডস স্ট্রিটের সরকারি অতিথিশালা। মাগনা থাকা নয়, তবে যে কোনও হোটেলের চেয়ে অর্ধেকের অর্ধেক টাকায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ওখানে। সৌমিত্র মিত্রকে আমাদের আগমনের হেতুটি জানাই যে শান্তিনিকেতনের বসন্তউৎসব আমাদের দেখা হয়নি, তাই দেখতে আসা। দলবল নিয়ে সৌমিত্র মিত্রও যাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে, বললেন এক সঙ্গেই যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন তিনি। বসন্ত উৎসবে শান্তিনিকেতন চললাম সবাই। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে রাজকীয় একটি কামরায় আমরা উঠে বসি। জানালায় পর্দা, চেয়ারে গদি, কাঠের আসবাবে নিপুণ কারুকাজ! রেলগাড়ির কোনও কামরা যে এমন সুন্দর হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। সৌমিত্র জানালেন এই কামরায় বসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বোলপুর যাওয়া আসা করতেন। আনন্দ ধরার জায়গা নেই আর, রবীন্দ্রনাথ সারা হৃদয় জুড়ে। সৌমিত্র মিত্রর দলে অশেষ, মোনা আর নাচের মেয়ে রেখা মৈত্র। অশেষ আর মোনা আমার কাছাকাছি বয়সের। রেখা মৈত্র কিছুটা বয়সে বড়। আমার দলে রাকা আর আলতাফ, আলতাফ লোকটি লাজুক, ভাবুক, উদাসীন হলেও রাকা খুব চটপটে, বুদ্ধিমতি, সাহসী, হিসেবী। রাকা রাজশাহীর মেয়ে, কথায় পাকা। আলতাফ ধীরে হাঁটেন, দাঁড়ালে ত্রিভঙ্গ দাঁড়ান, ধীরে বলেন,কম বলেন কিন্তু যখন বলেন ভাল বলেন। দুজনেরই আমার চেয়ে দশ বারো বছর বেশি বয়স। বয়স আসলে কোনও ব্যপার নয়। ছোট বড়তে বেশ ভাল বন্ধুত্ব হতে পারে। ভেবেছিলাম সাত জন মিলে আড্ডা দিয়ে পথ পার হব। কিন্তু কি করে কি করে যেন আমরা আলাদা হয়ে গেলাম, আমরা বাঙালরা একদিকে, ঘটিরা আরেকদিকে। নিরীহ তিনটি বাঙাল বেশির ভাগ সময় চুপচাপ বসে থেকে সৌমিত্র মিত্রর দলটির হৈ হল্লা দেখি। বাঙালরা খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পারে না ঘটিদের সব আচরণ। ধরেন, বলেন, শোনেন, করেন, হাঁটেন বলে অভ্যস্ত আমরা, দমদমে নেমেই এ কারকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে হ্রস্ব উকারের কাঁধে সওয়ার হই বটে, তবে জিভ সবসময় কথা শোনে না। দু একটি হ্রস্ব উকারের পর আবার এ কার উড়ে এসে বসে। আমাদের উচ্চারণ নিয়ে, গ্রাম্যতা নিয়ে, অজ্ঞতা নিয়ে কসমোপলিটন শহরের আলট্রামডার্ন ক্যালকেসিয়ানদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারি না। আমাদের জড়তা, কুণ্ঠা সবই ঘটিদের কাছে মজার জিনিস। মুখ খুললেই মজার জিনিস হয়ে উঠি বলে মুখ যথাসম্ভব বন্ধ করেই রাখা ভাল। যদি খুলতেই হয় মুখ, নিজেদের মধ্যেই খুলি। শান্তিনিকেতনে নেমে যেহেতু আমি আগে এসেছি এখানে, আমি অনেকটা বিশেষরি মত রাকা আর আলতাফকে রবীন্দ্রনাথের চারদিক দেখাই। রবীন্দ্রনাথের বাড়িঘর উঠোন আম্রকাননে হেঁটে বেড়াই। রাতে সৌমিত্র মিত্র আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি ঘরগুলোর একটিতে আলতাফ আর রাকা, একটিতে মোনা আর অশেষ, একটিতে রেখা মৈত্র আর আমি, আরেকটিতে একা সৌমিত্র মিত্র। গানের সূরে ঘুম ভাঙে ভোরবেলা। ‘ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল,জলে স্থলে বনতলে লাগল যে দোলঞ্চ শুনে হৃদয়ে দোল লাগে। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে হলুদ রঙের একটি শাড়ি পরে নিই। রাকা অনেক আগেই তৈরি হয়ে বসে আছেন। ঘটিরা তখনও ঘুমে। অনেক রাত অবদি অতিথিশালার ছাদে মদ্যপানের আসরে বসে ছিলেন, ঘুম থেকে উঠতে দেরি তো হবেই কিন্তু বাঙালদের তা সইবে কেন, আমরা তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উৎসবের একটি কণাও অদেখা রাখতে চাই না। অস্থির হয়ে হাঁটাহাঁটি করি বারান্দায়। ডাকাডাকিতে সৌমিত্র মিত্র ওঠেন। স্নান সেরে কাপড় পরে নাস্তা খেয়ে বেরোন তিনি আমাদের নিয়ে। এই দেরীটুকু সয় না আমার। মন ভাল হয়ে যায় উৎসবের আনন্দ দেখে। বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে মেয়েরা সব উৎসবে মেতে আছে। মঞ্চে মঞ্চে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া চলছে, এদিকে রবীন্দ্রনাথের নৃতনাট্য তো ওদিকে কবিতা পাঠ। চারদিক ছুটে বেড়াই। গান হচ্ছে, গায়ে গায়ে আবীর ছড়ানো হচ্ছে। আমার মুগ্ধ চোখ কোনও গানে ও আবীরে উচ্ছ্বসিত মানুষ থেকে সরেনি। এত গভীর করে এর আগে বসন্তকে গ্রহণ করিনি আমি। এর আগে বসন্তের উতল হাওয়া এমন লাগেনি গায়ে। এমন বাসিনি ভাল পৃথিবীর আলো, হাওয়া, মাটি ও মানুষ। গা পেতে সকলে সকলের আবীর নিয়েছে। মাঠে, আম্রকুঞ্জে, কলাভবনে, সঙ্গীত ভবনে আবীর ছড়ানোর উৎসবে সকলের কণ্ঠে ছিল গান, সকলের শরীরে ছিল নৃত্য। শান্তিনিকেতনের আলাদা একটি ঘ্রাণ আছে, জানি না কোত্থেকে এক ঘ্রাণ এসে প্রাণ ভরিয়ে দেয়। আমি রবীন্দ্রনাথে ডুবে থাকি, আবীরে ডুবি। এত কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখলে আশ্চর্য এক অনুভূতি হয়। আমার অনুভবগুলোর আবীর আমাকে রাঙিয়ে তোলে। রঙ খেলায় অভ্যস্ত নই, কাউকে রঙ না ছিটোলেও আমার গায়ে অচেনা অচেনা মানুষেরা রঙ ছিটিয়ে দেয়। অন্য দিন হলে ভীষণ রাগ করতাম, সেদিন রাগ করিনি। দেখি আরও আরও কবিরা রঙে ডুবে আছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও। কখন যে রাকা আর আলতাফকে হারিয়ে ফেলেছি ভিড়ে জানি না। তবে একা হয়ে যাই না। অনেকে যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসে আন্তরিক হয়ে ওঠে। রাতে গানের উৎসবে দেখা হয় তিন তরুণ কবি সৈয়দ হাসমত জালাল, গৌতম ঘোষ দস্তিদার আর চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। চৈতালির কবিতা আমি সেই কতকাল আগে সেঁজুতিতে ছাপতাম। অনেক রাত অবদি আমরা রিক্সা করে ঘুরে বেড়াই শান্তিনিকেতনের আশেপাশে। কোপাই নদীর ধারে বসে পূর্ণিমা রাতের মোহন রূপ দেখি। ঢাকা শহরে থেকে পূর্ণিমা কখন যায়, কখন আসে তার কিছুই টের পাই না। ঢাকার বাইরে সুদূর বোলপুরে আমি যেন আমার কৈশোরটি ফিরে পাই। জালাল, গৌতম, গৌতমের প্রেমিকা উর্মিলা আর আমি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, সৌমিত্র মিত্র তাঁর দল নিয়ে তারাপীঠের মন্দির ঘুরে এসেছেন। আমার ভাবতে অবাক লাগে সৌমিত্র মিত্র ধর্মে বিশ্বাস করেন। আমি হয়ত ভেবেই নিয়েছিলাম আমার কলকাতার বন্ধুরা কেউই আস্তিক নয়। অবশ্য আস্তিক না হলে যে উপাসনালয় দেখতে যাওয়া যায় না, তার কোনও কথা নেই। আমি নিজেই তো কত মন্দির মসজিদ দেখতে গিয়েছি, অবশ্য গিয়েছি ভেতরের কাণ্ড কারখানা দেখতে। কে কী উদ্দেশ্য নিয়ে মন্দির মসজিদে যায় সেটি বোঝা দায়। গোপনে গোপনে কার মনে কি আছে কে জানে! ঢাকাতেও এরকম, মাঝে মাঝে কারও কারও ধর্ম বিশ্বাসের খবর শুনে আঁতকে আঁতকে উঠি। আল মাহমুদের মত শক্তিশালী কবিও একদিন শুনি পাঁড় ধার্মিক। পান্না কায়সার মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত, তিনিও ভক্তিভরে কোরান পড়েন। বুদ্ধিজীবী মুনতাসির মামুন শুক্রবার মসজিদে যান জুম্মাহর নামাজ পড়তে।
গভীর রাতে শান্তিনিকেতনের সেই অতিথিশালায় আমার ঘুম ভেঙে যায়। একটি পুরুষকণ্ঠ শুনি রেখা মৈত্রর সঙ্গে চাপা স্বরে কথা বলছে। বিছানায় ধস্তাধস্তির মত একটি শব্দ পেতে থাকি। আমি চোখ বুজে পড়ে থাকি, কাউকেই বুঝতে দিই না আমি যে জেগে আছি, আমার জেগে থাকা, আমার টের পাওয়া যেন কাউকে বিব্রত না করে। একসময় দুটি প্রাণীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনি। নিঃশব্দে উঠে ভেজানো দরজাটি বন্ধ করে দিই ভেতর থেকে। বাকি রাত আমি ঘুমোতে পারি না। কি অদ্ভুত রহস্যে মোড়া এই জগত! দিনের আলো ফুটলে সব আবার পরিস্কার হয়ে ওঠে। মানুষগুলোকে অনেক চেনা লাগে। নতুন হওয়া বন্ধুদের আরও প্রাণবান মনে হয়। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা ফিরে যাওয়ার পর জালালের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে বেশ কয়েকবার। জালাল আমাকে এত সহজে আপন করে নেয় যে মনে হয় তার সঙ্গে আমার অনেককালের বন্ধুত্ব। কলকাতার মানুষগুলো দ্রুত তুমি করে সম্বোধন করে ফেলে, তাইতেই এমন মনে হয়। তুমি সম্বোধনটির কাঁধে চড়ে এক লাফে দুশ কিলোমিটার দূরত্ব পার হওয়া যায়। কিডস স্ট্রিট থেকে খুব বেশি দূরে থাকে না জালাল। এসি মার্কেটের মাথায় একটি ছোট্ট ঘরে থাকে, মার্কেটের সিকিউরিটি অফিসারের চাকরি করে। আমাকে নিয়ে একদিন সে বেরোয় ময়দানে হাঁটতে। তার দাদার বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যায়। পার্ক সার্কাসের ঘিঞ্জি এলাকায় যাওয়া হয়নি আগে কখনও, কলকাতার এক অন্য রূপ দেখা হয় আমার। জালাল মুসলমান ছেলে, মুসলমান ধর্মে নয়, নামে। মুসলমান নামের কারণে কি করে ভুগতে হয় জালালকে, তার দাদাকে, তার আত্মীয় স্বজনকে তার করুণ কাহিনী সে বর্ণনা করে। তার দাদা সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ বড় লেখক, কিন্তু তাঁকে যেমন করে ওপরে ওঠানো হয়েছিল, তেমন করেই নাকি ভূতলে ফেলেও দেওয়া হয়েছে। যে কোনও একজন মুসলমান লেখক হলেই চলে আনন্দবাজারের, তাই মুস্তফা সিরাজকে বাদ দিয়ে আবুল বাশারকে নিয়ে চলছে হৈ চৈ। ফুলবউ নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন তিনি। বইয়ের প্রচারও হচ্ছে খুব। জালাল আমাকে ভেতরের কথা শোনায়, মুস্তফা সিরাজকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশেই নাকি আবুল বাশারকে তোলা হচ্ছে। কদিন পর বাশারকে পছন্দ না হলে তাঁকেও বসিয়ে দেওয়া হবে। বাংলা সাহিত্যের আকাশে কোন নক্ষত্র জ্বলজ্বল করবে, আলো নিবিয়ে দিয়ে কোন নক্ষত্রকে চুপসে ফেলা হবে তা নির্ধারণ করার মালিক হচ্ছে দেশ আর আনন্দবাজার গোষ্ঠী। জালালের হতাশার গহ্বর থেকে ছিটকে বেরোতে থাকে ক্ষোভ। শামসের আনোয়ারের বাড়ি গিয়েছিলাম একবার, শামসের আনোয়ার নামী কবি, তাঁরও দেখেছি রাগ হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের ওপর। যত হিন্দু আর মুসলমান নামের সাহিত্যিকদের আমি দেখি কলকাতায়, কেউই ধর্ম মানেন না। কিন্তু তারপরও হিন্দু সাহিত্যিকদের প্রতাপে মুসলমান সাহিত্যিকরা কোণঠাসা বোধ করেন। এ কেবল সাহিত্যের জগতে নয়, সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই একই চিত্র। সংখ্যাগুরু হিন্দু সংখ্যালঘু মুসলমানকে মোটেও সভ্য মানুষ বলে গণ্য করে না। জালালের বর্ণনা শুনি আর বাংলাদেশের হিন্দুদের কথা মনে হতে থাকে আমার। এখানে মুসলমান আর ওখানে হিন্দু একইরকম যন্ত্রণা ভোগ করছে। আমার কাছে কে হিন্দু, কে মুসলমান সে কখনই কোনও বিষয় নয়। কোনও শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, সে কোনও ধর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। পিতামাতার ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয় যে কোনও মানুষই। কোনও এক কালে মুত্যুভয়ে, অনিশ্চয়তার আশঙ্কায়, ক্ষমতার লোভে কিছু বুদ্ধিহীন এবং কিছু কুবুদ্ধির লোক ধর্ম নামক একটি জিনিস তৈরি করেছে। ধর্ম ছড়িয়েছে এক গোত্র থেকে আরেক গোত্রে, এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে। মানুষ সব সময় যে য়েচ্ছ!য় কোনও ধর্ম গ্রহণ করেছে তা নয়, জোর জবরদস্তি করে ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষের ওপর। ধর্মের কারণে যুদ্ধ বেঁধেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে । ভারতবর্ষে হিন্দুত্ব, ইসলাম, ক্রিশ্চান ধর্ম সবই ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছে। সেই কত কাল আগে কিছু লোক ভারতবর্ষে ঢুকেছিল, বেদ রচনা করেছিল! বসে বসে এরপর অসভ্য কিছু নিয়ম তৈরি করেছে, শ্রেণী ভেদ করেছে, জাত বর্ণ ভাগ করেছে, মানুষের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে, মেয়েদের নিকৃষ্ট আখ্যা দিয়ে পুঁথি রচনা করেছে। কত সহস্র বছর কেটে গেছে, আজও সেই নিয়ম ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক পরম শ্রদ্ধাভরে পালন করছে। কত নির্বোধ হলে উঁচু জাত আর নিচু জাতের সংজ্ঞায় মানুষ বিশ্বাস করতে পারে! এই জাত ভেদের আবর্জনায় ধর্মের ব্যাধি আরও জেঁকে বসেছে। একসময় নিম্নবর্ণ হিন্দুরা উচ্চবণগ হিন্দুর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম বা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। মুসলমান বাঙালিদের মধ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে কেউ কেউ দাবি করে তারা আশরাফ, তারা আতরাফ নয়। আতরাফ হল নিচু জাত। আশরাফ বড় জাত, মধ্যএশিয়া থেকে আগত মুসলমানের উত্তরসুরি। আশরাফদের অনেকে সে কারণে উর্দু চর্চা করে। যেসব মুসলমান বাংলা বলে, তারা নিম্নবর্ণ হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া। বাংলা বলতে তাই উঁচু মুসলমান জাতের বড় আপত্তি। আমার বলতে কোনও সংকোচ হয় না যে আমি উঁচু শ্রেণীর নই, আমি আতরাফ, নিম্নবর্ণ হিন্দু, হিন্দু জমিদার বা হিন্দু রাজার অত্যাচারে কোনও এক কালে হিন্দুধর্ম ছেড়ে আমার পূর্বনারী বা পূর্বপুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বাংলা আমার ভাষা, আমার সংস্কৃতি। আমি গৌরব বোধ করি আমার বাঙালিত্ব নিয়ে। ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মানুষই ইতিহাস ঘাঁটে না। ঘাঁটলে মানুষে মানুষে ধর্মের বিভেদ, জাত বর্ণের বিভেদের মত বর্বরতা অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এই ভারতবর্ষের মুক্তচিন্তার মানুষেরা বলে গেছেন সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। দুশ বছর আগে লেখাপড়া না জানা লালন ফকির নামের এক লোক জাতের বিভেদকে তুচ্ছ করে মানবতার গান গেয়ে গেছেন। আর আজ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা লোক জাত নিয়ে মাথা ঘামায়! দেখলে অবাক লাগে। মানুষ তো জানি সামনের দিকে এগোয়, আলোর দিকে। পেছনের অশিক্ষা অজ্ঞতা আর অন্ধকার আঁকড়ে রেখে কী সুখ পায় তারা!
জালালের ক্ষোভের সঙ্গে যে কোনও অত্যাচারিতের ক্ষোভই মেলে। কিডস স্ট্রিটের বাড়িটির বারান্দায় বসে অন্ধকার কলকাতার দিকে কালো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি। ভোর হলেই কলকাতা আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠবে। কলকাতা এত সুন্দর, এত আন্তরিকতা মানুষের, এত প্রাণের ছোঁয়াচ চারদিকে, এত ভালবাসি কলকাতাকে কিন্তু একটি তথ্য শুনে আমার মন খারাপ হয়ে যায় যে এ শহরে হিন্দু আর মুসলমান পাশাপাশি বাড়িতে বাস করে না। বেশির ভাগ মুসলমানই একটি নির্দিষ্ট এলাকায় থাকে। বাড়িঅলা হিন্দু হলে কোনও মুসলমানকে বাড়িভাড়া দেয় না। বাংলাদেশে এরকম কোনও নিয়ম নেই। হিন্দু মুসলমানের জন্য আলাদা আলাদা এলাকা নেই। যে কারও অধিকার আছে যে কোনও এলাকায় বাস করার। বড় বড় দালান উঠছে ঢাকা শহরে। দোতলায় হিন্দু, তিনতলায় মুসলমান, চারতলায় বৌদ্ধ, পাঁচতলায় খ্রিস্টান বাস করছে। এতে কারও কোনও আপত্তি করার কিছু নেই। বাংলাদেশে যে কোনও হিন্দুর কাছে মুসলমানের ধর্মানুষ্ঠান, রীতি নীতি কিছুই অপরিচিত নয়। মুসলমানের কাছে হিন্দুর বারো মাসে তেরো পুজোর কিছুই অজ্ঞাত নয়। অজ্ঞাত নয় কারণ তারা একজন আরেকজনের প্রতিবেশী। কলকাতার মুসলমানরা হিন্দুর পরব অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান রাখলেও হিন্দুরা জানে না মুসলমানের সব আচার অনুষ্ঠানাদির খবর। কলকাতায় একটি প্রশ্ন অনেকে করে, তুমি মুসলমান না বাঙালি? যেন মুসলমান হলেই অবাঙালি হতে হবে, যেন বাঙালি মানেই হিন্দু! কলকাতায় অনেক অবাঙালি মুসলমান বাস করে, তা ঠিক। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা তো কম নয়। মুসলমান নাম দেখেই তাকে অবাঙালি ভাবার রেওয়াজ অশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে খুব বেশি। মেলামেলা না থাকলে এ-ই হয়। বাংলাদেশে যাদের আনাগোণা আছে, বাঙালি হিন্দু যারা বাঙালি মুসলমানদের সংস্পর্শে এসেছে, তারা এই ভুলটি সহসা করে না। তারপরও আমি দেখেছি কলকাতার বাঙালি মুসলমানের ক্ষোভের শেষ নেই। ক্ষোভের কারণটি আমি বুঝি। সংখ্যালঘু হিসেবে বেঁচে থাকার হাজারো সমস্যা। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা কি কম নির্যাতন ভোগ করছে! যদি আমি তুলনা করি, বলব, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানরা অনেক আরামে আছে বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দুদের চেয়ে। দীর্ঘবছর যাবৎ বামপন্থী সরকারের শাসন চলছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। এই সরকার সংখ্যালঘু মুসলমানের সবরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে। মুসলমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের কোনও ব্যবস্থা নেই ভারতে, কিন্তু বাংলাদেশে রাষ্ট্রই সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করে। রাষ্ট্র থেকেই সংখ্যালঘুদের জন্য কোনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় না। বাংলাদেশ হতে পারত একটি সাম্প্রদায়িক কলহমুক্ত দেশ। কারণ দেশটিতে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করছে, কারণ মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ কোরানে কি লেখা আছে তা নিরানব্বই ভাগ মুসলমানই জানে না যেহেতু তাদের ভাষা আরবি নয়, জানে না বলেই তারা জানে না বিধর্র্মীদের উপেক্ষা করার কথা, জানে না বলেই জানে না বিধর্মীদের কচুকাটা করার কথা, কারণ পাশাপাশি বাস করলে সহমর্মিতা গড়ে ওঠে পরষ্পরের মধ্যে, কারণ হিন্দু মুসলমানের জন্য কোনও ইশকুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা নয়, কারণ হিন্দু মুসলমানে বিয়ে হয়, কারণ হিন্দু মুসলমানে বন্ধুত্ব হয়, কারণ তারা বাঙালি, কারণ তাদের ভাষা এক, কারণ তাদের সংস্কৃতি এক, কারণ কোনও অবাঙালি মুসলমানের সংষ্কৃতি বাঙালি মুসলমানের ওপর বর্ষিত হয়নি, কারণ বাঙালি মুসলমানের পুর্বপুরুষ নিম্নবর্ণ হিন্দু, কারণ দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে রয়ে যাওয়া হিন্দু বেশির ভাগই জমিদার নয়, জমিদারের প্রজা, প্রজায় প্রজায় মিল হয় রাজায় প্রজায় মিলের চেয়ে বেশি, কারণ বেশির ভাগ হিন্দুই ওদেশে দরিদ্র অথবা হিন্দু মুসলমানের ভেদ না মানা আদর্শবাদী মানুষ। এত সব কারণ থাকা সত্ত্বেও থেকে থেকে মুসলমান নামের মানুষেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দুদের ওপর, লুটপাট, ধর্ষণ ইত্যাদি চলে অবাধে। এর কারণ কি? কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণ সাপ বেরিয়েছে গর্ত থেকে। ধর্মান্ধ সাপ। একাত্তরে যুদ্ধের সময় যে সাপেরা পাকিস্তান কায়েম করতে চেয়েছিল, যে সাপগুলোর পূর্বপুরুষ ধর্মের নামে ভারতের ভাগ চেয়েছিল; সেইসব বিষাক্ত সাপ। একটি সাপই পারে একশ মানুষকে পিছু হটাতে। সংখ্যায় কত তারা! খুব বেশি নয়। কিন্তু সংখ্যা বাড়ছে, সংখ্যা বাড়ার শব্দ পাই, হিশহিশ শব্দ শুনি বাতাসে।
আমি ভারত ভাগ দেখিনি, ভারত ভাগের কষ্ট আমার ভেতরে গভীর করে বাসা বাঁধার কথা নয়। কিন্তু বাসা বাঁধে। ধর্ম নামক একটি মিথ্যের জন্য বিশাল একটি দেশের বিভক্ত হওয়ার কষ্ট আমি লালন করি, কষ্ট আরও ঘন হয় যখন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের দেখি, বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গে সহায় সম্পত্তি বাড়িঘর ফেলে চলে আসা উদ্বাস্তু। শূন্য থেকে গড়ে তুলেছে আবার সব। অনেকে সেই যে সাতচল্লিশ সালে দেশভাগের সময় চলে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে, ফিরে আর যায়নি পূবে। কেবল স্মৃতি রয়ে গেছে পুকুর ভরা মাছের, গোলা ভরা ধানের, দিগন্ত অবদি যত দূর চোখ যায় আম কাঁঠালের বনের। কলকাতার শহুরে বস্তিতে গাদাগাদি করে বাস করে পূর্ববঙ্গের স্মৃতি মধূর ঠেকে নিশ্চয়ই। কিন্তু কজন ভাবে ওদেশে যারা রয়ে গেছে, দারিদ্র বা আদর্শের কারণে যারা ওপার থেকে এপারে আসেনি, তারা কেমন আছে! এই ভাবার দায়িত্বটি বাংলাদেশ নামের নতুন একটি দেশের নতুন মানুষের। কেবল ভাবা নয়, প্রচুর কাজও আছে করার। প্রথম ভারত ভ্রমণের পরই উথলে পড়া আবেগ থেকেই কয়েকটি কবিতা লিখেছিলাম দুই বাংলার অভিন্নতা নিয়ে, কাঁটাতারের নির্মমতা নিয়ে, ভারত ভাগের মিথ্যে নিয়ে। ধর্ম ধর্ম করে যে ভারত ভাগ হল, মুসলমানের জন্য পাকিস্তান নামে দুই খণ্ডের একটি দেশ হল, কই মুসলমানরা তো এক দেশে বাস করতে পারেনি! একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হওয়াই তো প্রমাণ করেছে ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। আমার কবিতাগুলো ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত সাপের দল আমাকে অবলীলায় দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। মৌলবাদিদের পত্রিকায় আমাকে গালাগাল করে প্রায়ই লেখা বেরোয়। কখনও পড়া হয়, কখনও হয় না। যার যা ইচ্ছে লিখুক, আমার কিছু যায় আসে না। আমি আমার অনুভবের কথা লিখে যাবো। আমি আমার অন্তর্গত বিষাদের কথা, বেদনার কথা লিখে যাবো। আমি আমার স্বপ্নের কথা অসংকোচে লিখে যাবো। একটি অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন আমি গোপনে গোপনে দেখি, না হলেও অখণ্ড একটি বাংলার স্বপ্ন আমার হৃদয় যমুনায় সাঁতার কাটে।
কলকাতায় এসেই চেনা পরিচিত বন্ধুদের জন্য আনা উপহার বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসি। খুব ভাল লাগে উপহার দিতে মানুষকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন শিশুর মত খুশি হয়ে ওঠেন ফতুয়া পেয়ে, দেখে খুব আনন্দ হয়। উপহার দেওয়ার স্বভাবটি, আমার বিশ্বাস, আমি মার কাছ থেকে পেয়েছি। মাকে যতই অপছন্দ করি আমি, রক্ত বলে একটি ব্যপার আছে, রক্তের মধ্যে তিনি খানিকটা হলেও আছেন। মা এরকম নিজের যা কিছু আছে অন্যকে বিলিয়ে দিয়ে সুখ পান। নিজের খুব বেশি কিছু নেই মার। না টাকা পয়সা, না গয়নাগাটি, না শাড়ি কাপড়। নিঃস্ব মাকে বারবারই দেখি আরও নিঃস্ব হতে। মার এই বেহিসেবী উদার হওয়া দেখে মার ওপর সময় সময় রাগ করি আমি। একটি শাড়ি হয়ত দিলাম মাকে, মা দুদিন খুব খুশি হয়ে শাড়িটি পরলেন, কদিন পরই দেখি সেই শাড়ি গদার মার গায়ে। গদার মার শাড়ি নেই, ত্যানা পরে ভিক্ষে করতে আসে, দেখে মা দিয়ে দিয়েছেন শাড়িটি। ইয়াসমিনেরও দেখি হাত হয়েছে দেওয়ার। কিন্তু মার মত এমন নিজেকে নিঃস্ব করে নিঃস্বার্থ হতে আমি বা ইয়াসমিন কেউই পারি না। দাদা আর ছোটদা পেয়েছেন বাবার স্বভাব, পাই পয়সার হিসেব করেন। তাঁরা বাবার চেয়েও কয়েক কাঠি ওপরে। বাবা অন্তত গরিব রোগীদের বিনে পয়সায় চিকিৎসা করেন। আসলে চিকিৎসা করা বাবার নেশা। পয়সা পাবেন না বা কম পাবেন বলে তিনি প্রেসক্রিপশন লেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন না। শহরের ধনী গরিব সকলেই বাবার চিকিৎসায় ভাল ফল পেতেন, এখনও পান, কিন্তু বাবার চেম্বারে ভিড় এখন আগের চেয়ে অনেক কম, বেশির ভাগই দূর দূরান্ত থেকে আসা চেম্বারের বারান্দায় পাতা চেয়ারগুলোয় চামড়া- ফাটা পা তুলে বসে থাকা গরিব রোগী। ময়মনসিংহে নতুন নতুন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আসার পর ধনী রোগীরা এখন তাঁদের কাছেই যান। পুরোনো অভিজ্ঞ ডাক্তার বাবার কাছে অবশ্য আসেন কেউ কেউ, বিশেষজ্ঞের চিকিৎসায় সুস্থ না হলে তবে আসেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক, চেহারা দেখেই বলে দিতে পারেন যক্ষা হয়েছে, এক্সরে করার দরকার পড়ে না। বাবার মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার চাকরি, চেম্বারে রাত বারোটা পর্যন্ত রোগী দেখার ব্যস্ততা, তারপরও ফাঁক পেলেই তিনি তাঁর পুরোনো ডাক্তারি বই পড়েন। যেদিন ক্লাস থাকে, তার আগের রাতে বাড়িতে রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। বাবার ব্যস্ত জীবনটি আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করেছে। আমার নিজের জীবনটিকে বসে থাকা শুয়ে থাকার আলস্য না দিয়ে এই যে ব্যস্ত করে তুলেছি, ব্যস্ততায় বাবার মত আনন্দ পাচ্ছি, সেটি তো বাবার কাছ থেকেই পাওয়া। বাবা মার কত রকম স্বভাব যে আমাদের রক্তে আর মস্তিস্কে ঘাঁপটি মেরে থাকে, ধীরে ধীরে সেই স্বভাবগুলো আমাদেরই অজান্তে আমাদের চরিত্রের অন্তর্গত হয়ে যায়। আমার নিজের চরিত্রটির ব্যাখ্যা আমি অনেকসময় করতে পারি না। একসময়ের লাজুক মেয়ে, যে মেয়ে অচেনা মানুষ দেখলে লুকোতো, দিব্যি সে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, কথা কম বলা মানুষটি মুখে খই না ফোটাতে পারলেও দিব্যি গড়গড় করে কথা বলছে। আগের আমি আর এই আমিকে মোটেও মেলাতে পারি না। কলকাতায় চেনা পরিচিতদের সংখ্যা বাড়ছে। কলকাতাকেও ঢাকার মত আপন মনে হয়। বড় বড় লেখক শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বেশি। বিশেষ করে যদি হৃদয়বান কেউ হয়। ইন্দ্রনাথ মজুমদারের মুখের সরল হাসিটি দেখে তাঁকে বড় আপন মনে হয় আমার। চমৎকার আলাভোলা মানুষ এই ইন্দ্রনাথ। সুবর্ণরেখা নামে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটেও একটি বইয়ের দোকান আছে তাঁর। দোকানটি খুঁজে পেতেই আমার সময় লেগেছে অনেক। দোকান পাওয়া গেল কিন্তু সেটি এত ছোট যে দাঁড়াবার জায়গা নেই। পুরোনো বইয়ে ঠাসা ঘরটি। পুরোনো বই বিক্রি করেন ইন্দ্রনাথ, নতুন বইও ছাপেন, তবে আলতু ফালতু কোনও বই নয়, বইএর মত বই হলেই ছাপেন। ব্যবসার চেয়ে আদর্শই বেশি কাজ করে বই ছাপার পেছনে। একটি ভাল বই পেলে সে বই হয়ত বিক্রি হবে না খুব, তবু আর কেউ না ছাপলেও তিনি ছাপেন। যেদিন দুপুরে গেলাম ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে, তিনি বেরিয়ে পড়লেন আমাকে নিয়ে কড়া রোদ্দুরে। বললেন ‘খাচ্ছেন তো বড় বড় জায়গায়, আজ চলুন আপনাকে একটা খুব ভাল জায়গায় নিয়ে যাই।’ ভাল জায়গাটি কোথায়? ভাল জায়গাটি হল এক এক উড়ের দোকান। উড়ের দোকানে বসে কলাপাতায় মাছভাত খাই দুজন। খুব অল্প পয়সায় খাওয়া। এই খাওয়াতে যে আনন্দ পেয়েছি, তা ঝকঝকে দামি রেস্তোরাঁয় বসে পাইনি।
কলকাতায় অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। রবীন্দ্র সদনে, শিশির মঞ্চে, কলা মন্দিরে, একাডেমিতে কিছু না কিছু হচ্ছেই। রবীন্দ্রসদনে কবিদের কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান হল একদিন। সৌমিত্র মিত্র আলতাফ হোসেন আর আমাকে ঢুকিয়ে দিলেন কলকাতার কবিদের সঙ্গে মঞ্চে বসে কবিতা পড়ার জন্য। কলকাতার মঞ্চে আগে কবিতা পড়েছি, আড়ষ্টতা তাই কমই ছিল এবার। আলতাফ হোসেনের জন্য প্রথম পড়া কলকাতায়, লাজুক মানুষটি স্বর ওঠাতে পারলেন না তেমন, গালে আর গলায় ওঠানো আঙুলকেও নামাতে পারলেন না কবিতা পড়ার সময়। বাংলাদেশের কবিদের কলকাতায় বেশ খাতির করা হয়। মুসলমান নামের মানুষগুলো অন্য দেশ থেকে এসে বাংলায় কথা বলছে, বাংলায় কবিতা পড়ছে, দেখতে হয়ত অনেকে মজা পায়। কারও কারও আছে করুণার চোখ। বেচারা বাংলাদেশিদের পিঠে দাদাগিরির কয়েকটি চালিয়ে যাও, মন্দ হচ্ছে না জাতীয় স্নেহের চাপড় পড়ে। কেউ কেউ আবার বাংলাদেশের যে কোনও ব্যপারে অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত। বাংলাদেশের ধুলো বালি জল কাদা এনে দিলেও গায়ে মাখবে। পশ্চিমবঙ্গের কিছুই ভাল নয়, যত ভাল সব ওই বাংলাদেশ নামের দেশটিতে, আবেগের তাড়নায় এমন কথাও বলে ফেলে। বাঙালদের খানিকটা চিড়িয়া, খানিকটা মানুষ, সরল সহজ, আন্তরিক, অতিথিপরায়ণ, দুহাতে খরচ করতে পারা, বেহিসেবী, অলস, আরামপ্রিয়,খানেঅলা, দানেঅলা, পকেট ভারিঅলা, কিছু কম জানেঅলা, কিছু কম বুঝনেঅলা বলে মনে করা হয়। অনুষ্ঠানে নতুন অনেক কবি আর আবৃত্তিকারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন সৌমিত্র মিত্র। জয় গোস্বামীর মত প্রতিভাবান কবির সঙ্গে সামান্য হলেও কথা হয়। গায়ে মেদ মাংস নেই আধা সন্ন্যাসী গোছের মানুষটি আজকাল কী চমৎকার কবিতা লিখছেন! শরীরে প্রতিভা থাকে না। প্রতিভা মস্তিস্কের কোষে কোষে জন্ম থেকেই বাস করে। আমার অনুর্বর মস্তিস্কে যতই জল সার ঢালি না কেন, জয়ের প্রতিভার শতভাগের একভাগও গজাবে না। যার হয় তার হয়। সকলের হয় না। সকলের হলে সকলেই কবি হত। প্রতিভা থাকলে শরীরে মাংস কমাবার বা বাড়াবার দরকার পড়ে না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত বিশাল বপুর লোকও প্রতিভার কারণে সুদর্শন হয়ে ওঠেন। হাড়গিলে জয়কে হাড়গিলে বলে মনে হয় না। নিজের পেচ্ছ!বের অসুখ নিয়ে যতই তিনি দুঃখ করুন, তাঁকেই মনে হয় একশ লোকের মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান।
সৌমিত্র নিজে আপাদমস্তক ঘটি হয়েও বাঙালদের জন্য সময় না থাকলেও সময় তৈরি করে সময় দেন। সৌমিত্রর সঙ্গে মিত্রতা না থাকলে কলকাতায় স্বচ্ছন্দে চলাফেরা সহজ হত না। আমাদের সারাক্ষণের সঙ্গী না হলেও অন্তত তিনি বলে দেন কী প্রয়োজন হলে কোথায় যেতে হবে। একা একা ঘুরে ঘুরে পথ হারাতে হারাতে আর খুঁজে পেতে পেতে শহর চেনা যায়, গাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে শহর সত্যিকার চেনা যায় না। আমার ভাল লাগে ভিড় ভাট্টায় হেঁটে বেড়াতে, সরু সরু পুরোনো গলিতে ঢুকে মানুষের জীবন দেখতে, রাস্তার কলের জলে স্নান করা মানুষ দেখতে, ভাল লাগে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে, কলেজ স্ট্রিটের বই পাড়ায় হেঁটে হেঁটে বই কিনতে, গড়িয়াহাটের ফুটপাত থেকে শাড়ি কিনতে। কত কী যে করার আছে কলকাতায়! সাধ মেটার আগে সময় ফুরিয়ে যায়। কেবল তো শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব দেখতে আর রবীন্দ্র সদনে কবিতা পাঠ উপভোগ করতে পশ্চিমবঙ্গে আসিনি। কিছু দায়িতও্ব আছে কাঁধে। লাল কালো বইটি পৌঁছে দিতে হবে শ্রী শ্রীপান্থকে, বেলাল চৌধুরী বলে দিয়েছেন। কাঁধের দায়িত্বটি নিয়ে প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে আনন্দবাজার আপিসে রাকা আর আলতাফকে নিয়ে ঢুকি, উদ্দেশ্য দুটো, শ্রীপান্থকে লাল কালো বইটি দেওয়া আর শংকর লাল ভট্ট াচার্যকে একটি নির্বাচিত কলাম দেওয়া। শংকর লাল ভট্টাচার্য সানন্দা পত্রিকায় চাকরি করেন, একবার ঢাকা গিয়েছিলেন, তখন পরিচয় হয়েছিল, কলকাতাতেও দেখা হয়েছিল আগের বার। তিনি আনন্দবাজারর ছাদে বসে সাহিত্যিক অনেক বিষয় নিয়ে অনর্গল বলছিলেন, যার বেশির ভাগই আমার মাথায় ঢোকেনি। তবে একটি জিনিস ঢুকেছিল, তা হল মানুষটি বিদেশি সাহিত্য বেশ পড়েছেন, মাথায় কিলবিল করছে বিদ্যে। পড়ুয়া লোক যত দেখি কলকাতায়, তত কিন্তু ঢাকায় দেখি না। বাঙালি হিন্দুর পড়ার অভ্যেস অনেককালের। বিদ্যাচর্চায় বাঙালি হিন্দু বাঙালি মুসলমানের চেয়ে একশ বছর এগিয়ে আছে। মেঘচ্ছদের ভাষা পড়ব না বলে বাঙালি মুসলমান অহংকার করেছিল, বাঙালি হিন্দু করেনি। সেটির প্রভাব তো কিছুটা থাকবেই। শ্রীপান্থ কোন ঘরে বসেন, বারান্দায় হাঁটতে থাকা একজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিই। ঘরের দরজা ঠেলি ভয়ে ভয়ে, ভয়ে ভয়ে এ কারণে যে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঘরগুলোয় জ্ঞানের ভাণ্ডারগুলো গম্ভীর গম্ভীর মুখ করে বসে থাকেন, আবালের মত ঢুকে কোনও গভীর কিছুতে কারও তন্ময় হয়ে থাকাকে নষ্ট করে দিই যদি! ঘরে ঢুকে দেখি গোল মুখের একটি ছোটখাটো লোক আর দুজন গোল মুখের চেয়ে অল্প বয়সের, বসা। তিনজনই লিখছেন।
‘এখানে কি শ্রীপান্থ বলে কেউ আছেন?’ জিজ্ঞেস করতেই গোল মুখের মধ্যবয়ষ্ক লোকটি কাগজ থেকে মাথা তুলে কলম থামিয়ে বললেন, আমি শ্রীপান্থ।’
‘আমি ঢাকা থেকে এসেছি। বেলাল চৌধুরী আপনার জন্য একটা বই পাঠিয়েছেন।’
‘কি বই?’
‘লাল কালো।’
‘লাল কালো?’
বইটি তাঁর হাতে দিলে তিনি আমাকে বসতে বললেন। ভেবেছিলাম, বই পেয়ে ‘ঠিক আছে, ধন্যবাদঞ্চ বলে তিনি আমাকে বিদায় দেবেন। সে তো দিলেনই না, রাকা আর আলতাফকেও বসতে বললেন তিনি। বইটি হাতে নিয়ে শ্রীপান্থ বেশ খুশি। পাতা উল্টো ছবিগুলো দেখে মুখে হাসি ফুটছে তাঁর। বললেন ‘কলকাতায় তো লাল কালোর রিপ্রিন্ট নেই, বাংলাদেশ থেকেই শেষ অবদি বইটি বেরোলো। কলকাতার কড়চায় আমি এর একটি খবর করে দেব।’ আনন্দবাজার পত্রিকায় কলকাতার কড়চা বিভাগটি শ্রীপান্থই দেখেন। তাছাড়া তিনি পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখেন প্রায়ই। ঘরের টলটল করা প্রতিভা অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় আর গৌতম রায়কে শিখিয়ে পড়িয়ে তুখোড় সাংবাদিক বানাচ্ছেন। কি নাম আপনার, কোথায় বাড়ি, কি করেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর তসলিমা, ময়মনসিংহ, ডাক্তারি সবিনয়ে উল্লেখ করি। রাকা আর আলতাফের পরিচয়ও দেওয়া হয়।
চা আসে। দুধ চা। খেতে খেতে শ্রীপান্থ বললেন তাঁর বাড়িও ময়মনসিংহে। দেশভাগের সময় চলে এসেছেন এপারে।
‘ময়মনসিংহের কোথায়?’ আমার কণ্ঠে সিংহের আগ্রহ।
‘ধোবাউড়া।’
ধোবাউড়া ছেড়ে সেই যে চলে এসেছেন আর ফিরে যাননি কোনওদিন। পূর্ববঙ্গ থেকে ভারত ভাগের পর যারা চলে এসেছিলেন এদেশে, তাদের অনেকের মত শ্রীপান্থেরও আর ফিরে যাওয়া হয়নি দেশের মাটিতে। ইচ্ছে করেন যাবেন একবার, দেখে আসবেন কেমন আছে দেশটি। ইচ্ছে থাকলেও সকলের হয় না যাওয়া। বাাংলাদেশ থেকে এলে পূর্ববঙ্গের কিছু লোক বেশ খাতির করেন। শ্রীপান্থও আমাকে খাতির করলেন। খাতির করা মানে বসতে বলা, নাম ধাম জিজ্ঞেস করা। বাড়ি কোথায়, কি করি, জিজ্ঞেস করা, চা খাওয়ানো। সবই করেছেন তিনি। এবার বিদায় নেবার পালা। যখন বিদায় নেব, জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কি লেখেন টেখেন নাকি?’
শুনে আমার কান লাল হয়ে উঠল। যৎসামান্য লিখি বটে, কিন্তু তা নিশ্চয়ই উল্লেখ করার মত নয়, বিশেষ করে এমন পণ্ডিত ব্যক্তির সামনে। আমার পক্ষে বলা সম্ভব হয় না যে আমি লিখি। আলতাফ বলেন, ‘ও লেখে। ও তো বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে।’ ‘তাই নাকি!’
শ্রীপান্থ ওরফে নিখিল সরকার মুচকি হাসলেন।
আমি লজ্জায় নখ খুঁটতে থাকি।
‘হাতে কোনও বই টই আছে?’
‘বই!’
‘আপনার লেখা কোনও বই আছে আপনার কাছে?’
ব্যাগের ভেতর একটি নির্বাচিত কলাম আছে। বইটি শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্য। বড় সংকোচে ব্যাগ থেকে বইটি দেখতে দিই নিখিল সরকারকে। তিনি হাতে নিয়ে উল্টো পাল্টো বললেন, ‘আমার কাছে থাকুক এটা।’
মৃদু স্বরে বলি, ‘শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্য এনেছিলাম।’
‘আমাদের সানন্দার শংকর তো! ওকে পরে একটা দিয়ে দেবেন।’
ফটো তোলার এক লোককে ডেকে তিনি বললেন, ‘মেয়েটার একটা ছবি তুলে দাও তো! বাংলাদেশের মেয়ে, ওর বইয়ের একটা খবর করে দেব কড়চায়।’
সাদা আবার সাদাও নয়, সুতোয় আঁকা ছোট ছোট লাল কালো ফুলের তসরের শাড়ি পরা, কপালে একটি লাল টিপ, মুখে মলিন হাসি, ওভাবেই— ক্লিক। কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার বইয়ের খবর ছাপা হবে, তাও আবার ছবি সহ! আনন্দ করব কি, বিস্ময়ে বোবা হয়ে থাকি। বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিকদের জন্য দেশ আনন্দবাজারে চিরকালই নাগালের বাইরে। কখনও দেশ পত্রিকায় কারও কবিতা ছাপা হলে নাক এমন উঁচুতে ওঠে, যে বছর পার হলেও সে নাক স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে না। এই যখন অবস্থা, তখন আমার মত পুঁচকে নতুন লেখক বিস্ময়ে বোবা হবে না কেন!
বিস্ময়ে বোবা কত আর হয়েছি সেদিন! আমার জন্য সহস্রগুণ বিস্ময় অপেক্ষা করছিল কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসার কিছুদিন পর। ফিরে এসে হাসপাতালের ডিউটি, ফাঁকে চার পাঁচটে পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখা, মাঝে মাঝে প্রকাশকের তাগাদার উপন্যাস রচনা করা, এসব নিয়ে চলছিল। হঠাৎ চিঠি। চিঠি আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে। নির্বাচিত কলাম বইটির জন্য দেশ আনন্দবাজারের ১৯৯২ সালের আনন্দ পুরষ্কার আমাকে দেওয়া হচ্ছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি। আবার পড়ি চিঠি। আবারও। চিঠি কি ভুল করে আমার কাছে এসেছে! কিন্তু আমার নামটিই তো লেখা চিঠির ওপর। স্বপ্ন দেখছি না তো! না, স্বপ্নেরও তো সীমা আছে, আমার স্বপ্ন এত সীমা ছাড়িয়ে কখনও যায়নি। আমি যে আনন্দ-চিৎকারে বাড়ি ফাটাবো, সে জিনিসটিও করতে পারি না। বোবা হয়ে আছি। রক্ত চলাচল থেমে আছে বিস্ময়ে। বাংলা সাহিত্যে আনন্দ পুরষ্কার হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুরষ্কার। সবচেয়ে নামী। সবচেয়ে দামী। বাংলাদেশের কেউই এ পর্যন্ত এ পুরষ্কার পায়নি। আর আমি সেদিনের এক লেখক, তাও শখের লেখক, শখে কবিতা লিখি, প্রয়োজনে কলাম লিখি, আমি কি না পাচ্ছি এই পুরষ্কার! কী করে সম্ভব এটি! অসম্ভব অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা। আমি ঠিক বুঝে পাই না আমি কি করব। একবার বসি, একবার দাঁড়াই। একবার আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে অবাক চোখে দেখি, এ ঠিক আমি তো! পেচ্ছ!ব চাপে। মাথা ঘুরতে থাকে। বোবা হয়ে থাকার পাট চুকলে বাড়িতে এক মিলনই ছিল, তাকেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলি, ‘মিলন আমি আনন্দ পুরস্কার পাইছি।’ আনন্দ পুরস্কার ঠিক কি জিনিস, মিলন জানে না। এটি যে যায় যায় দিনের রচনা পুরস্কার জেতার মত নয়, এ যে অন্য কিছু খুব বড় কিছু অসম্ভব রকমের বড় তা বুঝিয়ে বলার পর মিলন হাঁ হয়ে থাকে। মিলন বোনের স্বামী হলেও আমার কাছে ঠিক বোনের স্বামী নয়, ছোট ভাই গোছের কিছু। চিঠিটি হাতে নিয়ে মিলনকে বলি, ‘তাড়াতাড়ি রেডি হও।’ মিলন দ্রুত লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট পরে নেয়। প্রথমেই খোকার বাড়িতে যাই। খোকা ডাকাডাকি শুনে বাইরে বেরোলে চিঠিটি হাতে দিয়ে উল্লসিত কণ্ঠে বলি, ‘আনন্দ পুরষ্কার, খোকা ভাই। আমি আনন্দ পুরষ্কার পাচ্ছি।’ খোকা মলিন হাসেন। কেন হাসিতে মালিন্য, বুঝি না। খোকার তো খুশিতে উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কথা। আমার যে কোনও সাফল্যে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন খোকা। সেই খোকার কেন এই অখুশি মুখ! কেন প্রাণহীন একটি হাসি তিনি উপহার দিলেন আমাকে! খোকা কি তবে ভাবছেন, আমি আকাশ ছুঁয়ে ফেলছি, এত বেশি উঁচুতে ওঠায় তাঁকে খুব ক্ষুদ্র লাগছে দেখতে! খোকা কি ভাবছেন তিনি আর কখনও আমার নাগাল পাবেন না! জানি না কেন। খোকার নির্লিপ্তি আমার মন খারাপ করে দেয়। সুখবরটি বেলাল চৌধুরীকে জানানোর জন্য আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার সইছিল না। রাত হয়ে গেছে, তবুও খুঁজে খুঁজে বেলাল চৌধুরীর বাড়ি বের করে ঢুকি। আমাকে দেখে চমকালেন তিনি, আগে কখনও তাঁর বাড়ি যাইনি। এত রাতে হন্তদন্ত হয়ে তাঁর বাড়ি যাওয়ার কারণ তিনি বুঝতে পারছেন না। ‘বেলাল ভাই, আমাকে আনন্দ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। চিঠি এসেছে। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। কি রকম যেন লাগছে।’
চিঠিটি বেলাল চৌধুরীর হাতে দিই। তিনি পড়ে উচ্ছঅ!স প্রকাশ করেন। বউকে বলেন আমাকে মিষ্টি মুখ করাতে। ব্উ মিষ্টি খেতে দেন। আমার কি আর মিষ্টিতে মন! বেলাল চৌধুরীর হাতে আমার এই বিস্ময় আর আনন্দ ভাগ করে দিয়ে আমি হালকা হই। কখনও কোনও কোনও আনন্দের বোঝা একা আমার পক্ষে বহন করা দুঃসহ হয়ে ওঠে।
‘আমি কি এত বড় পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বেলাল ভাই?’
‘নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তুমি ভাল লিখছো। নিশ্চয়ই তুমি যোগ্য। ওরা তো আর তোমার মুখ দেখে পুরষ্কার দেয়নি! বুঝলে, আনন্দ পুরষ্কার হচ্ছে বাঙালি সাহিত্যিকদের জন্য স্বপ্নের বিষয়। আনন্দ পুরষ্কার হচ্ছে গিয়ে বাংলার নোবেল প্রাইজ।’
খোকার নির্লিপ্তি যতটা আমাকে যে কষ্টটুকু দিয়েছিল, বেলাল চৌধুরীর উচ্ছঅ!সে সেই কষ্ট মুছে যায়। কিন্তু বাড়ি ফিরে সারারাত আমার ঘুম হয় না। অনেক রাত্তির পর্যন্ত একা একা জেগে বসে থাকি। আজ যদি রুদ্র বেঁচে থাকত! রুদ্র নিশ্চয়ই আমার জন্য গর্ববোধ করত। পূর্বাভাসে আমার কলাম পড়ে রুদ্র একবার চিঠি লিখেছিল , সে চিঠি ছাপাও হয়েছিল পূর্বাভাসের চিঠিপত্র কলামে। লিখেছিল তার সঙ্গে যা হয়েছে আমার তার দায় সে বহন করছে, আমি যেন তাকে ক্ষমা করে দিই এবং সমস্ত পুরুষজাতিকে আমি যেন নিস্তার দিই এমন হেনস্থা থেকে। আহা রুদ্র! আমি তোমার ওপর রাগ করে একটি বাক্যও লিখছি না। সমস্ত পুরুষজাতির বিরুদ্ধে আমি লড়ছি না। আমি কেবল সমাজের নষ্ট নিয়মের বিরুদ্ধে লড়ছি, যে নিয়ম নারীকে দাসী করে, পণ্য করে, যৌনসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করে, নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা না দেওয়ার জন্য সমাজ, রাষ্ট্র আর ধর্মের ষড়যন্ত্রের আমি প্রতিবাদ করছি। যখন লিখি আমি কাঁদি, আমার জন্য নয়, কাঁদি ওই সুফিয়া খাতুনের জন্য, যাকে ধর্ষণ করে মাটির তলায় জ্যান্ত পুতে ফেলেছে কিছু লোক, ফরিদার জন্য, যে মেয়ে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি হয়নি বলে পাড়ার এক ছেলে ফরিদার মুখে এসিড ছুঁড়ে পুড়িয়ে দিয়েছে মুখ, সখিনা বানুর জন্য যার বাবা বিয়েতে যথেষ্ট যৌতুক দিতে পারেনি বলে স্বামী তাকে মেরে হাত পা ভেঙে তালাক দিয়েছে, শরিফা খাতুনের জন্য, কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে যাকে দা দিয়ে কুপিয়ে মেরেছে স্বামী, কাঁদি নুরজাহানের জন্য, যে মেয়ে এক পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলেছে বলে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে লোকেরা, ফুলমতির জন্য, যে মেয়েকে প্রেম করার অপরাধে লোকেরা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। আমি তো ভালই আছি, শহরের বড় হাসপাতালে ডাক্তারি করি, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, জীবনের যে কোনও সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নিই, নিজে যেমন পছন্দ করি, তেমন জীবন যাপন করি। আমার মত কজন মেয়ে এমন প্রচণ্ড বেঁচে আছে! কিন্তু আমি কখনও ভুলে যাই না যে আমি সুফিয়া খাতুনের মত, নুরজাহানের মত, সখিনা বানুর মত একজন। আমারও হতে পারত যা হয়েছে ওদের।
পুরস্কার আনতে এবারের আমন্ত্রণ অন্যরকম। যাওয়া আসার টিকিট, কলকাতায় থাকা সবই এখন আনন্দবাজারের দায়িত্ব। আহলাদে মাটিতে পা পড়ে না আমার। মুই যেন কি হনুরে জাতীয় একটি ভাব যখন আমাকে গ্রাস করছে,তখনই বইটির দুটো কলামের কথা মনে করে আঁতকে উঠি। কেউ যেন ধারালো একটি সুই দিয়ে খোঁচা দিয়ে আমার ফুলে ওঠা অহংকারকে চুপসে দিল। বেদ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে, যদিও আমার কাছে সব কটি বেদ এর খণ্ড ছিল তারপরও বেদ বিশেষজ্ঞ সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রাচীন ভারত ও বৈদিক সমাজ বই থেকে না টুকে পারিনি। কী এক ঘোরের মধ্যে বাক্যের পর বাক্য টুকে নিয়েছি। বইটি আমাকে এমনই প্রভাবিত করেছে যে আমি পারিনি নিজেকে সুকুমারী থেকে মুক্ত করে নিজের আলাদা কোনও মত প্রকাশ করতে। সুকুমারী থেকে বেদের অনুবাদটুকুই নিতে পারতাম, কিন্তু তাঁর মন্তব্যও চুরি করতে গেলাম কেন! চুরি করতে গেলাম এই জন্য যে তাঁর মতের সঙ্গে আমার মত হুবুহু মিলে যায়। এমন সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি বেদএর শ্লোকের যে বইটি না পড়লেও ঠিক এমনই ব্যাখ্যা আমার মনে উদয় হত। আমার কথাই যেন তিনি আমার বলার আগে বলে দিয়েছেন। কলাম দুটো পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পর ক্ষীণ একটি গ্লানি আমাকে নিস্তার দেয়নি। ব্যপারটি এক বালতি খাঁটি দুধের মধ্যে দুফোঁটা চোনা মিশিয়ে পুরো দুধকেই নষ্ট করে দেওয়ার মত। আনন্দ পুরস্কারের খবর পেয়ে প্রথম আমার মনে পড়েনি আমার এই চুরির কথা। হঠাৎ যখন মনে পড়ে, গ্লানি আর লজ্জা আমাকে কেঁচোর মত নিজের গর্তে ঢুকিয়ে রাখে। ঘৃণায় নিজের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। সে রাতেই বেরিয়ে পড়ি টেলিফোন আপিসে গিয়ে কলকাতায় জরুরি একটি ফোন করার জন্য। নিখিল সরকারকে ফোনে জানাই যে আমার এই নির্বাচিত কলাম পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নয়, কারণ বইটির ভেতরে দুটো কলাম আছে, যেখানে সুকুমারী ভট্টাচার্যের বই থেকে অনেক কিছু নেওয়া হয়েছে। আমার এই স্বীকারোক্তি শোনার পর যদি তিনি বলতেন যে তিনি পুরস্কার কমিটিকে ব্যপারটি অবগত করে আনন্দ পুরস্কারটি আমাকে যেন না দেওয়া হয় তার জন্য তদবির করবেন, হালকা হতে পারতাম। তাঁকে মনে হল না তিনি আদৌ আমার এই চুরি নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন। জানি চুরি অনেকেই করে। সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম লেখাটি, তিনি নিজেই বলেছেন, চুরি করে লেখা। দাঁড়ি কমাও বাদ দেননি চুরিতে। কিন্তু আমার তো এটি প্রথম লেখা নয়। রীতিমত যখন নাম করে ফেলেছি লিখে, তখন চুরি করা। আমাকে আমিই ক্ষমা করতে পারছি না, অন্যরা কি করে করবে! পুরস্কার পেলে মানুষের আনন্দ হয়, আমার হচ্ছে লজ্জা। নিখিল সরকারকে সুকুমারী-তথ্যটি জানিয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া না দেখে লজ্জার ওপর ভয় এসে ভর করে। তবে কি পুরস্কারটি আমাকে নিতেই হবে! কী করে মুখ দেখাবো আমি! কী করে এই লজ্জা আমি ঢাকবো! চেতনার জানালা দরজায় শব্দ হতে থাকে প্রচণ্ড, আমি কী এমন লেখক যে এত বড় একটি পুরস্কার পাবো! এতকাল যাঁরা আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা আমার চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ ভাল সাহিত্যিক। তাঁরা জ্ঞানের সমুদ্র, আমার জ্ঞান নেই, গুণ নেই, তুলনায় আমি এক বিন্দু জল। বাংলাদেশের কাউকে যদি পুরস্কার দিতে হয়, তবে আর যাকেই হোক, আমাকে তো দেওয়ার প্রশ্ন ওঠার কথা নয়। এত বড় মাপের সাহিত্যিক এ দেশে আছেন, এত বড় কবি আছেন, তাঁদের সাহিত্যের সঙ্গে আমার কোনও গদ্য পদ্যের কোনও তুলনা করাও হাস্যকর। শওকত ওসমান, রশীদ করীম, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন, রাহাত খান, বশীর আল হেলাল —-এঁদের পায়ের ধূলার যোগ্য নই আমি। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতার ধারে কাছে কি আমার কবিতা স্থান পেতে পারে! নিঃসন্দেহে বলতে পারি, না। তবে আমি কেন নির্বাচিত হলাম! পুরস্কার কমিটির মাথাটি নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে, অথবা বাংলাদেশের লেখকদের সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, তা না হলে পুরস্কারের জন্য আমাকে নির্বাচন করতেন না। কমিটিতে খুব বড় বড় লেখক বুদ্ধিজীবী আছেন, এ কেমন বুদ্ধির নমুনা! জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, হুমায়ুন আজাদের মত বড় প্রাবন্ধিক যদি এই পুরস্কার না পান, তবে কী যোগ্যতা বলে আমি এই পুরস্কার পাই! কিছু শখের কবিতা লিখেছি, পত্র পত্রিকায় কিছু কলাম লিখেছি, এরকম তো কত কেউ লেখে, সাহিত্যিক জগতের অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে আমার, তাই বলে তো আমি সাহিত্যিক হয়ে যাইনি! সে স্পর্ধাও আমি করি না। কলকাতার কত বড় বড় লেখকও এখন পুরস্কারের মুখ দেখেন নি, আর আমাকে কি না নিজে উপস্থিত থেকে নিজে হাতে নিতে হবে পুরস্কার! পুরস্কারের ঘোষণাটি আমাকে হঠাৎ যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কত ক্ষুদ্র আমি, কত অযোগ্য আমি, লেখক হিসেবে কত তুচ্ছ আমি, কত অপাংক্তেয় আমি! মেয়েদের স্বাধীনতার জন্য লিখি, কিন্তু আমি তো নতুন লিখছি না, অনেকেই মেয়েদের অধিকারের পক্ষে লিখেছেন, লিখছেন। আমাকে তো কোনও স্বার্থত্যাগ করতে হয়নি, আমাকে ভুগতে হয়নি, পথে নামতে হয়নি, সংগ্রাম করতে হয়নি, অনেকে তো কত রকম সংগঠন করেছেন নির্যাতিত মেয়েদের সাহায্য করার জন্য। এনজিও খুলেছেন, ইশকুল বানিয়েছেন, নিজের যা কিছু আছে সবই বিসর্জন দিয়েছেন নারী উন্নয়নের জন্য। আমি কিছুই করিনি। এখনও পরিবেশ প্রতিবেশ থেকে শেখা বাড়ির কাজের মেয়েদের গালে চড় কষানোর, পিঠে ধুমাধুম কিল দেওয়ার বদভ্যাস ছাড়তে পারিনি। সুফির দেড়বছর বয়সী মেয়েটি প্যানপ্যান করে কাঁদত বলে, চতুর হাসি হাসত বলে সুফির আড়ালে আমি একদিন তার হাতদুটো মুচড়ে দিয়েছিলাম। আমার এই হাত কলুষিত হাত, এই হাতে এত বড় সম্মানের প্রতীক ওঠা মানায় না। যে সব আদর্শের কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি বার বার, সেইসব আদর্শের কতটুকু জীবনে চর্চা করেছি! সমাজতন্ত্রের রূপরেখা পড়ে আমি উৎসাহিত হই, কিন্তু নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করার উৎসাহ কোনওদিন পাইনি। দেশের আশি ভাগ মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে জেনেও নিজের আরাম আয়েশের কিছু ছাড় দিই না। হাজার হাজার মানুষ ফুটপাতে বা তক্তপোষে ঘুমোচ্ছে জেনেও তো আমি নিজে নরম গদিতে ঘুমোবার লোভ ছাড়তে পারি না। কেউ না খেয়ে আছে বলে নিজেকে তিনবেলা খাওয়া থেকে বঞ্চিত করি না। সমাজতন্ত্র নিয়ে যা কিছু আমার মনে, সবই মধ্যবিত্তের রোমান্টিকতা। মেয়েদের নিয়ে যা কিছু এ যাবৎ লিখেছি, নিজের দিকে থুতু ছিটিয়ে বলি, হয় টাকা কামাবার জন্য, নয় নাম কামাবার জন্য! লেখক হিসেবে যেমন নিকৃষ্ট আমি, মানুষ হিসেবেও তেমন।
সব জেনে বুঝেও কলকাতা রওনা হই। পুরস্কারের চিঠি পাওয়ার পর পরই পুরস্কার গ্রহণ করার সম্মতি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলাম আনন্দ বাজারে। পাঠিয়েছিলাম বলে যে আমার করার কিছু ছিল না তা নয়। আমি ইচ্ছে করলেই কি বলতে পারতাম না যে না আমি যোগ্য নই এই পুরস্কারের, আমি নেব না পুরস্কার! পুরস্কার নিতে অস্বীকার করার জন্যও যে স্পর্ধা দরকার হয়, সেই স্পর্ধাটি আমার নেই কেন! জীবনে স্পর্ধা করে তো অনেক কিছুই করেছি। ভেতরে ভেতরে কি একটি লোভ কাজ করছে না আমার! আমি যত নিজেকে বলতে চাই, না করছে না, কিন্তু নিজের খুব গভীরে কোথাও সূক্ষ্ম সুপ্ত বাসনার গন্ধ পাই। লজ্জা ভয় সব কিছুর তলে খুব গোপন একটি লোভ আমাকে নিভৃতে কামড়ায়। অপরাধীর মত একটি অন্যায়ের দিকে আমি যেতে থাকি, চোখ কান বন্ধ করে একটি সর্বনাশা নদীতে আমি ঝাঁপ দিই, নিজেকে সংবরণ করার কোনও শক্তি আমার মনেতে নেই। নিঃশক্তি, নিঃসহায় আমিটি সজোরে নিঃশ্বাস নেয় নির্লোভ হতে। আমি অশ্লীল শব্দ লিখি, আমি যৌন-লেখিকা, নগণ্য লেখিকা, লেখালেখির কিছুই জানি না, আমি কিছু না, আমি কিμছু না শুনে শুনে, অবমাননা আর অসম্ভ্রম পেয়ে পেয়ে নিজে ভুগতে ভুগতে আত্মীয় স্বজনকে ভোগাতে ভোগাতে যদি হঠাৎ শক্ত কিছু মাটি পাই মাথাটি, যে মাথাটি বার বার নুয়ে নুয়ে যায় লোকের ভৎসর্না আর বিদ্রূপে, উঁচু করে দাঁড়াবার, অসম্মাননা ছুঁড়ে ছুঁড়ে যারা আমাকে অμছুত করেছে, তাদের যদি দেখানোর সুযোগ হয় নিজের সামান্যও সম্মান, তবে আমি সুযোগটি কেন ছেড়ে দেব! পায়ের তলার মাটি যতটা শক্ত হলে দাঁড়ানো যায়, তার চেয়েও বেশি শক্ত করে মেয়েমানুষকে দাঁড়াতে হয়, নিজের যোগ্যতার প্রমাণ পুরুষকে যতটা দিতে হয়, তার চেয়ে বেশি দিয়েই মেয়েমানুষকে কাতারে দাঁড়াতে হয়— আমার মেয়েমানুষ পরিচয়টিতে তাই আমি একটি অহংকার জুড়ে দিতে চাই, যে অহংকারটি আমাকে কারও ধাককা দিয়ে ফেলে দেওয়া থেকে, দূর দূর করে তাড়ানো থেকে, চোখ মুখ নাচিয়ে কৌতুক করা থেকে বাঁচাবে, বাঁচাবে আর সাহিত্যের জগতে, যে জগতে আমার বিচরণ, যে জগতটি মূলত পুরুষের, স্থান দিতে বাধ্য হবে। আমি নির্লোভ হতে পারি না।
কলকাতায় পৌঁছে দেখি আমার জন্য একটি সুন্দর হোটেল ঠিক করা আছে। সুন্দর হোটেলে সুন্দর একটি ঘর। আনন্দ পাবলিশার্সে আমাকে ডাকলেন বাদল বসু। আনন্দ থেকে আমার নির্বাচিত কলাম বইটি ছাপা হবে। এত কিছু কি সইবে আমার! এত প্রাপ্তি! কালো পাহাড়ের মত শরীর বাদল বসুর; তাঁর হাসিহীন গম্ভীর মুখটি দেখলেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। বাদল বসু কঠিন কঠিন মুখে কঠিন কণ্ঠে আমাকে বই প্রকাশের নানা রকম কাগজে সই করতে বললেন। এসব সইয়ে আমার অভ্যেস নেই। ঢাকায় বই ছাপা হয়, কোনও লিখিত ব্যপার থাকে না, সবই মৌখিক। কত পারসেন্ট রয়্যালটি দেওয়া হবে লেখককে, কত পারসেন্ট প্রকাশক নেবে, কখনও উল্লেখ করা হয় না। কাগজে টাকার অংকের কোনও ঘরের দিকে তাকাই না আমি। যেখানে যেখানে সই করতে বলা হয়, মুখ বুজে সই করি। সবকিছু আনুষ্ঠানিক এখানে। সবকিছুতেই একশ রকম নিয়ম। আমার বই ছাপা হতে যাচ্ছে বাংলা সাহিত্যের সব চেয়ে বড় প্রকাশনী থেকে, এই সুখেই তো আমি বগল বাজাবো। আমার কাছে পারসেন্ট কোনও বিষয় হবে কেন! আনন্দপুরষ্কারের টাকা ছিল এর আগে পঞ্চাশ হাজার, এ বছর বেড়ে এক লাখ হয়েছে। সেই টাকার জন্যও কয়েকটি সই নিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে সুবীর মিত্র। এক লক্ষ টাকার চেক পাব আমি, যে আমি জীবনে এত টাকা একসঙ্গে দেখিনি কোনওদিন। তবু এক লক্ষ টাকা আমার কাছে নিতান্তই গৌণ। পুরস্কারের মূল্যই সবচেয়ে বেশি। টাকার অংক দিয়ে এই পুরষ্কারের বিচার করা যায় না। টাকা পড়ে থাকে টাকার মত। যখন শেষ সইটি করি বই প্রকাশনার কাগজে, তখনই খবর আসে সত্যজিৎ রায় মারা গেছেন। বাদল বসু বেরিয়ে যান তক্ষুনি। আমার সারা শরীর শোকে অবশ হতে থাকে। ছবি দেখা আমার নেশা, যত ছবি সারা জীবনে দেখেছি আমি, সবচেয়ে ভাল লেগেছে সত্যজিৎ রায়ের ছবি। এক পথের পাঁচালিই আমি দেখেছি পনেরোবার। তবু সাধ মেটেনা। যতবার দেখি ততবারই দুর্গার জন্য কাঁদি, ততবারই অপুর জন্য মায়া হয়, ততবারই ইন্দির ঠাকুরণের জন্য হৃদয় ভেঙে যায়। ঢাকার অনেক লেখক কবিই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন কলকাতায় এসে। নিজে যেচে আজ অবদি বড় কোনও লেখক শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হতে যাইনি। সাহস বা স্পর্ধা কোনওটাই হয়নি। সত্যজিৎ রায়কে দেখা হয় আমার স্বচক্ষে, নন্দনে যখন তিনি শুয়েছিলেন ফুলের বিছানায়, তখন। আর তিনি ছবি বানাবেন না, আর তিনি ক্যামেরায় লুক থ্রো করবেন না। আর তিনি ছবি আঁকবেন না, গল্প লিখবেন না। মৃত্যু জিনিসটির মত ভয়ংকর কিছু আর নেই পৃথিবীতে। জীবনের কী অর্থ যদি একদিন হঠাৎ করে মরেই যেতে হয়! সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর কারণে আনন্দ পুরস্কার অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া হল একদিন।
কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলের বলরুমে আনন্দ পুরষ্কারের অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে। মঞ্চ সাজানো জুঁই ফুল দিয়ে, দেয়ালের কালো পর্দায় জুঁই ফুলে আঁকা মস্ত বড় কলম। এমন সুন্দর মঞ্চ আগে আমি কোথাও দেখিনি কখনও। ফুলের ঘ্রাণে ভরে আছে পুরো ঘর। আমন্ত্রিত রথী মহারথীরা আসন গ্রহণ করেছেন। ঘর ভরে আছে পণ্ডিতে, বিদ্যানে, বিশাল বিশাল লেখকে, কবিতে, শিল্পীতে। আনন্দ পুরষ্কার প্রতিবছর তিনজন পান। এবার দুজন কেবল। লেখক বিমল কর আর আমি। মঞ্চে আনন্দবাজারের সম্পাদক প্রকাশক অভীক সরকার, দেশ এর সম্পাদক সাগরময় ঘোষ এবং কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বসে আছেন। আরেকদিকে বসেছেন বিমল কর, আমাকেও বসতে হল তাঁর পাশে। অযোগ্য আমি কুণ্ঠিত আমি লজ্জিত আমি না পারছি চোখ তুলে মঞ্চ দেখতে, না পারছি দর্শকের দিকে তাকাতে। পুরষ্কার নেবার পর কিছু বলতে হবে আমাকে, ছেঁড়া একটি কাগজ আমার হাতের মুঠোয়, কাগজটি ঘামে ভিজে উঠছে, কাগজটিতে কাটাছেঁড়া লেখা, আগের রাতে লিখেছি পুরস্কার পাওয়ার পর বলার জন্য যা হোক কিছু। মঞ্চের বড় বড়রা এক এক করে বলছেন। ছোটটির বলার সময় যত ঘনিয়ে আসে, তত তার বুকের মধ্যে শব্দ করে বাজতে থাকে বিপদঘণ্টি। মাইকের সামনে দাঁড়ালে পা ঠকঠক করে কাঁপবে না তো! গলা কাঁপবে না তো কিছু বলতে নিলে! ভয়ে আবার মুর্ছা যাই কি না কে জানে। যখন ডাকা হল আমাকে, হাতের ঘামে ভেজা দলামোচা করা ছেঁড়া কাগজটি খুলে পড়ি, প্রথম নমস্কার শব্দটিও আমাকে কাগজের দিকে তাকিয়ে পড়তে হয়। গলা কাঁপা থামাতে গিয়ে উচ্চারণের ভুলগুলোকে থামাবার আমার উপায় থাকে না। পায়ের ঠকঠক বন্ধ করতে গিয়ে ছেঁড়া কাগজের শব্দগুলো একটি আরেকটিকে ঠোকরাতে থাকে। পড়ছি, যেন আল্লাহতায়ালার আদেশে পুলসেরাতে দাঁড়িয়ে বেহেস্ত বাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছি। .. আমাকে অনেকেই বলে আমি নাকি খুব আকাশ কুসুম কল্পনা করি। অলীক সব স্বপ্ন দেখি। গরম সইতে পারি না বলে নেপচুন গ্রহে চলে যাবার কথা ভাবি। ঘরে বসে পিঠে ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়াবার স্বপ্ন দেখি। ধরা ছোয়াাঁর বাইরে আমার এরকম নানা স্বপ্ন আছে। কিন্তু আমি কখনও এই স্বপ্ন দেখবার স্পর্ধা করিনি যে আমি হঠাৎ একদিন আনন্দ পুরস্কার পাবো। সুধীবৃন্দ, আমি আনন্দিত আমি অভিভূত। যে গ্রন্থটি আনন্দ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে সেটি মূলত নারীর ওপর ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অসভ্যতা আর অশালীনতা সম্পর্কে রাখঢাকহীন সরল উচ্চারণ। শাস্ত্র এবং সমাজ আমাদের এমন শিক্ষাই দেয় যে নারীর কোনও স্বাধীনতা থাকতে নেই। কিন্তু সেই নারী অবশ্যই মানুষ হিসেবে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয় যে নারী মনে এবং শরীরে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। মানুষের প্রধান প্রয়োজন স্বাধীনতা। নারীর এই স্বাধীনতাকে রাষ্ট্র অবরোধ করছে, নারীর স্বাভাবিক বিকাশে ধর্ম এখন প্রধান অন্তরায়। ধর্মের শৃঙ্খল আছে বলেই অধিকাংশ নারী আজ নিরক্ষর, উত্তরাধিকার বঞ্চিত, অধিকাংশ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, তালাক ও বৈধব্যের নির্যাতনের শিকার। পুরুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নারীত্ব, সতীত্ব, মাতৃত্ব ইত্যাদির সংজ্ঞা এবং মাহাত্ম্য তৈরি করেছে। এগুলো টিকিয়ে রাখতে পারলে সমাজে নারীর মূল্য বেশি। মূল্য এই অর্থে যে লোকে তাকে অপাংক্তেয় বা অস্পৃশ্য ঘোষণা করবে না। পৃথিবীতে প্রচলিত প্রতিটি ধর্মেই নারীর সতীত্ব রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু কোনও ধর্মেই পুরুষের জন্য কোনও সতীত্বের ব্যবস্থা করেনি। এর অর্থ এই, একগামিতা শুধু নারীর জন্য অবশ্য পালনীয়, পুরুষের জন্য নয়। তার জন্য আছে গণিকালয়ে যাবার অবাধ সুযোগ, তার জন্য চার বিয়ে হালাল করা হয়েছে ইসলাম ধর্মে, তার ভোগের জন্য ঘরের দাসিকেও বৈধ করা হয়েছে। পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য কুৎসিত অভিধায়। তাকে বন্দি করবার জন্য তৈরি করেছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, উদ্ভাবন করেছে ঈশ্বর, নিয়ে এসেছে প্রেরিত পুরুষ, লিখেছে ধর্মগ্রন্থ, অজস্র দর্শন, কাব্য, মহাকাব্য, সৃষ্টি করেছে সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ও আরও অসংখ্য শাস্ত্র। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বাংলায় নারীশিক্ষার যে ধারা শুরু হয়েছে, এর উদ্দেশ্য নারীকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত করা নয়, এর লক্ষ উন্নত জাতের স্ত্রী বা শয্যাসঙ্গিনী উৎপাদন। নারী শিক্ষাও প্রভু পুরুষেরই স্বার্থে। বিবাহ এখানে নারীদের পেশা। মনে করা হয় নারীর কল্যাণ শুভবিবাহে, সুখী গৃহে, স্বামীর একটি মাংসল পুতুল হওয়াকেই তারা মনে করে নারী জীবনের স্বার্থকতা। ইহুদি খিস্টান ও মুসলমানের মতে নারীর জন্ম পুরুষের পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে। মুসলমান মেয়েরা জানে স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত। জানে স্বামীকে তুষ্ট রাখতে পারলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা খুশি হন তাই বেহেস্তের লোভ দেখিয়ে স্বামীর পদসেবায় স্ত্রীদের নিয়োজিত রাখা একধরনের কৌশল, ধর্মের এবং সমাজের। বাঙালি মেয়েরা স্বামীর এঁটোকাঁটা খেয়ে ধর্মীয় পূণ্য অর্জন করে, এতে স্বামী সেবাও হয়, ধর্ম রক্ষাও হয়, কিন্তু যা হয় না তা হচ্ছে পুষ্টি রক্ষা। পুষ্টির অভাবে বাঙালি মেয়েরা অধিকাংশই স্বাস্থ্যহীন, শ্রীহীন এবং কিছুটা মেধাহীনও বটে। নারী কেবল পুরুষের যৌনসামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলাম ধর্মে নারীর যৌন অঙ্গ হিফাজত করবার কথা বলা হয়েছে। এও বলা হয়েছে নারী হচ্ছে পুরুষের শস্যক্ষেত্র, এই শস্যক্ষেত্রে পুরুষেরা যেন যেমন ইচ্ছে গমন করে। নারীকে অবাধ ভোগের কথা সকল ধর্মই বলেছে। নারীকে মূল্যবান সামগ্রী হিসেবে উপঢৌকন দেবার কথা, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত অঞ্চলের নারীকে ভোগের বস্তু করা সকল ধর্মেই স্বীকৃত। বাঙালি নারী কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর পরে, হাতে চুরি বা শাঁখা পরে এয়োতির চিহ্ন বহন করে। যদিও পুরুষের শরীর বিবাহের কোনও চিহ্ন বহন করে না। বৈধব্যের চিহ্নও নারী একা লালন করে। বিধবা নারীকে নানা রকম ব্রত পালন করতে হয়। পোশাক ও আহারে আমূল পরিবর্তন আনতে হয় কিন্তু বিপত্নীক কোনও পুরুষকে সঙ্গীহীনতার কোনও গ্লানি ভোগ করতে হয় না। নিরামিষ আহারের মূল কারণ বিধবা মেয়ের স্বাস্থ্যহীনতা ও শ্রীহীনতার পাশাপাশি যৌনাকাঙক্ষা নিবারণ করা, যদিও বিপত্নীকের জন্য এই সব অনাচার জরুরি নয়। সভ্যতার শুরু থেকে সমাজ ও ধর্ম মানুষকে পরিচালিত করেছে। সমাজ ও ধর্মের পরিচালক হিসেবে যুগে যুগে পুরুষেরাই কর্তৃত্ব করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্র তো বটেই, নারীকে সবচেয়ে বেশি অমর্যাদা করেছে ধর্ম। সামাজিক, অর্থতৈনিক ও রাজনৈতিক ভাবে যে হারে নারী নির্যাতিত হচ্ছে তাতে পুরো সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তন ছাড়া যেমন নারীর মুক্তি নেই, তেমনি ধর্মের শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা ছাড়াও নারীর মুক্তি অসম্ভব। মূলত এসবই আমার লেখার বিষয়। সমাজের পীড়িত, নিগৃহীত, দলিত, দংশিত নারীর জন্য লিখি। আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সীমান্ত পেরিয়ে এই বাংলায় কিছু মানুষের কানে পৌঁচেছে দেখে আমি উদ্বুব্ধ বোধ করছি। কারণ নারীর উক্তি সাধারণত কারও কানে পৌঁছতে চায় না, এমনকী নারীর কানেও নয়। সে কারণেই আমি চমকিত এবং অভিভূত। পশ্চিমবঙ্গকে কখনও আমার পৃথক একটি দেশ বলে মনে হয়না। একই ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ আমরা, আমরা একই জল হাওয়ার মানুষ, একই নদীর পাড়ে আমরা ঘরবাড়ি গড়েছি। এখানে এলেই আমার বুকের মধ্যে তীব্র এক যন্ত্রণা হয়, দেশ ভাগের যন্ত্রণা। আমার হৃদয়ে কোনও কাঁটাতার নেই। আমরা বাঙালি। বাংলা আমাদের ভাষা। আমরা আমাদের স্বজন আত্মীয়।
আজ এই আনন্দের দিনে আপনাদের জন্য নিবেদন করছি আমার ছোট্ট একটি কবিতা–
সাত সকালে খড় কুড়োতে গিয়ে আমার ঝুড়ি উপচে গেছে ফুলে
এত আমার কাম্য ছিল না তো!
এখন আমি কোথায় রাখি, কোথায় বসি, কোথায় গিয়ে কাঁদি!
পুরো জীবন শূন্য ছিল, ছিল!
কারও তো আর দায় পড়েনি দেবে।
তুমি এমন ঢেলে দিচ্ছ ভরে দিচ্ছ কাছে নিচ্ছ টেনে
এত আমার প্রাপ্য ছিল না তো!
আমাকে ক্ষমা করবেন।
আমি ক্ষমা চেয়েছি নিতান্তই ক্ষুদ্র হয়ে আকাশ ছোঁয়া একটি সম্মান নেওয়ার মত সাহস দেখিয়েছি বলে। আমি ক্ষমা চেয়েছি আমার স্পর্ধার জন্য, যে স্পর্ধায় যোগ্য না হয়েও এত বড় পুরস্কার আমি গ্রহণ করেছি। জানি না আমাকে কেউ ক্ষমা করেছেন কি না। আনন্দ পুরস্কার অনুষ্ঠানে অনেক লেখক শিল্পী আমাকে অভিনন্দন জানান। অনেকের সঙ্গে কথা হয়, যাঁদের সঙ্গে কখনও কোনওদিন কথা বলার সুযোগ হবে, কল্পনাও করিনি আগে। পরদিন আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় বেরোলো আনন্দ পুরষ্কার অনুষ্ঠানের খবর, অনুষ্ঠান মাতালেন তসলিমা ও ভীমসেন। চারদিকে আমাকে নিয়ে উৎসব শুরু হয়ে গেল। সৌমিত্র মিত্র খুবই আনন্দিত আমার আনন্দ প্রাপ্তিতে। তিনি আমাকে নিয়ে এদিক সেদিক যাচ্ছেন। একদিন চমকে দিলেন কণিকা বন্দোপাধ্যায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে। কণিকার গানের পাগল আমি। চোখের সামনে কণিকাকে দেখে আনন্দধারা বইতে থাকে আমার ভূবনে। বসন্ত উৎসবের সঙ্গী অশেষ আর মোনা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল হোটেলে। পটাপট কিছু ছবি তুলে নিয়ে গেল আমার সঙ্গে। আমি খুব মূল্যবান মানুষ হয়ে উঠলাম হঠাৎ। আনন্দবাজার পত্রিকার বারান্দায় আমাকে জড়সড় হয়ে হাঁটতে হয় না। দেখলেই লোকে চেনে আমি কে। সাগরময় ঘোষ দেশ পত্রিকায় আমাকে ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটি শুনে লজ্জায় মনে হয় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছি। আমি যে উপন্যাস লিখতে পারি না তা বললাম, তিনি হাসলেন। দাবিটি ছাড়লেন না। নিখিল সরকার তাঁর সল্টলেকের বাড়িতে আমাকে নেমন্তন্ন করলেন। আমাকে তিনি চিঠি দিয়ে পাঠালেন কিছু মূল্যবান মানুষের সঙ্গে দেখা করতে। বড় পুরস্কার পাওয়া ছোট লেখক চিঠি হাতে নিয়ে বড় সংকোচে বড় বড় মানুষের দ্বারস্থ হল। মহাশ্বেতা দেবী, মীরা মুখোপাধ্যায়….। আকাশে পৌঁছলে আকাশের নক্ষত্রদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা সম্ভবত ভদ্রতা। কিন্তু আমি কি সত্যিই আকাশে পৌঁছেছি, নাকি যে পাতালের আমি সে পাতালেই আছি! বেশ টের পাই আমি সেই পাতালেই আছি। নক্ষত্রদের সামনে আমি আমার তাবৎ অন্ধকার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কলকাতায় গুরুজনদের বিশেষ করে খুব বড় লেখক শিল্পীদের সকলে ঢিপঢিপ করে প্রণাম করে। আমি সামনে এসে বাঁশের মত দাঁড়িয়ে থাকি। প্রণামের অভ্যেস নেই বলে করতে পারি না। কদমবুসি নামে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যে প্রণাম প্রচলিত, সেটিও আমি করতে অভ্যস্ত নই। অশেষ শ্রদ্ধা মনে, অথচ হাত বাড়াচিছ না পায়ের ধুলোর দিকে, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুরা আমাকে একটি বেয়াদব মেয়ে বলে মনে মনে গাল দেন হয়ত, কিন্তু আমি কী করতে পারি!হঠাৎ করে আমাকে যদি বলা হয় তুমি হাল চাষ কর, আমি তো স্থবির দাঁড়িয়েই থাকব। যে জিনিস আমার দ্বারা হয়নি, তা হবেও না জানি। হাল চাষ করতে না পারি, কিন্তু গ্রাম্যতা আমার চরিত্রের গভীরে। ঢাকা থেকে আনা ছোটখাটো উপহার কলকাতার অনেককে দিতে আমার ভাল লাগে। অভীক সরকার আনন্দ পুরস্কার দিলেন আমাকে, তাঁকে তো বিনিময়ে একটি উপহার আমাকে দিতে হয়, এই গ্রাম্য সৌজন্য রক্ষা করতে গিয়ে যে শাড়িটি পরে পুরস্কার নিয়েছিলাম, সেই নানাবর্ণের চমৎকার জামদানি শাড়িটির আঁচল কেটে পার্ক স্টিটের একটি ভাল বাঁধাইএর দোকান থেকে দ্য বেস্ট সোনালী ফ্রেমে বাঁধাই করে নিয়ে মহা উৎসাহে দ্য বেস্ট উপহারটি নিয়ে যেদিন আনন্দবাজারে পৌঁছই, নিখিল সরকার আমার স্পর্ধা দেখে জিভ কাটলেন। মাথায় আমার যে বুদ্ধিটি ধরেনি তা হল অভীক সরকারের মত উচ্চ রুচির শিল্পবোদ্ধার ঘরে ভারতবর্ষের কোনও শিল্পীর আঁকা চিত্র যদি স্থান পায়, সে বড়জোর মকবুল ফিদা হোসেন, তাছাড়া বাকি সব নামী দামী পশ্চিমি শিল্পীদের চিত্রকলা, জামদানি শাড়ির আঁচল সে আঁচল যত সুন্দরই হোক না কেন, এটি তাঁর ঘরে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। মনে মনে বলি, যে মেয়েরা এই অপূর্ব সুতোর কাজগুলো করেছে, তারাও তো খুব বড় শিল্পী। শিল্পী হোক, ধনী এবং রুচিবানরা এসব তুচ্ছ জিনিসকে মূল্য দেন না। ভাল যে আমি অভীক সরকারের ঘরে উদ্ভট জামদানি চিত্রকলা নিয়ে উপস্থিত হইনি আগেই। নিখিল সরকার আমাকে বললেন, এটি যদি দিতেই চাই আমি তবে যেন অভীক সরকারের স্ত্রীকে দিই। শেষ অবদি লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁর স্ত্রীর জন্য আমার অতিতুচ্ছ উপহারটি দিয়ে বিশাল আনন্দবাজারের বিশাল অভীক সরকারকে বিশাল অপমানের হাত থেকে বাঁচাই।
বাংলাদেশ দূতাবাসের এক কর্মকর্তা কিছু লেখককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর বাড়িতে, আমাকেও জানিয়েছেন। মূলত আমার সম্মানে। আমি উপস্থিত হবার পর আমাকে ঘিরে বসে পড়ল কলকাতার কবি লেখকরা। এক একজন প্রশ্ন করছে, নানা কিছু নিয়ে প্রশ্ন— রেনেসাঁস, রেভ্যুলুশান, ফেমিনিজম, ব্যাকল্যাশ, মডার্নিজম, পোস্ট মডার্নিজম, আমার সাহিত্যিক ভাবনা, রাজনৈতিক আদর্শ, শ্রেণী সংগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষগুলোর চোখ আমার দিকে আগ্রহে উত্তেজনায় অপেক্ষায় অপলক হয়ে আছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি জ্ঞানী জ্ঞানী মানুষগুলোর দিকে। প্রশ্নগুলো বড় কঠিন লাগে আমার কাছে। আমার ফ্যালফ্যাল দেখে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। সংকোচে শামুকের মত গুটিয়ে যেতে থাকি। যদি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতাম এই সুধী সমাবেশ থেকে! যদি হঠাৎ নেই হয়ে যেতে পারতাম! আমাকে কোনও প্রশ্ন কোরো না, আমি কোনও প্রশ্নের উত্তর জানি না। মনে মনে বলি, তার চেয়ে আমাকে রহিমা বেগমের গল্প শোনাতে বল, কন্যাসন্তান জন্ম দিয়ে কি করে হতাশায়, বেদনায় ঘৃণায় আশঙ্কায় চিৎকার করে কেঁদেছিল রহিমা। আমাকে বল, আমি তেমন কেঁদে তোমাদের দেখাই। আমি বুদ্ধিজীবী নই। আমি মোটা মোটা বই পড়ে পৃথিবীর ইতিহাস ভুগোল, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য সংস্কৃতির জ্ঞান অর্জন করিনি। আমি বক্তা নই। গুছিয়ে কিছু বলতে পারি না। কায়ক্লেশে কিছু লিখি, রহিমা বেগমের আর্তনাদ আমাকে কাঁদায় বলে লিখি। এমন বড় বড় আসরে বড় বড় বক্তৃতা দেওয়ার যোগ্য আমি নই। আমি ময়মনসিংহের সাধারণ ঘরে সাধারণ ভাবে বেড়ে ওঠা সাধারণ মেয়ে। আমি গভীর তত্ত্বকথা বুঝি কম। আমার ঘটে বুদ্ধি কিছু কম ধরে। চিরকালই।
১৬. পক্ষে বিপক্ষে
আনন্দ পুরষ্কার পাওয়ার পর লেখক বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানান। কেউ কেউ জানান ঘৃণা। মৌলবাদী গোষ্ঠী প্রচার করছে যেহেতু আমি ইসলামের বিরুদ্ধে লিখি তাই বড় আনন্দে হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠী আনন্দবাজার আমাকে পুরষ্কার দিয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকা হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠীর পত্রিকা এ আমি আগে শুনিনি। এ যাবৎ যত লেখা আনন্দবাজার এবং দেশ পত্রিকায় পড়েছি, কখনও কোনও লেখা পাইনি যেখানে হিন্দু মৌলবাদীর পক্ষে কোনও কথা আছে বরং হিন্দু মৌলবাদীর বিপক্ষেই লেখা ছাপা হয় পত্রিকাগুলোয়। কেউ কেউ বলেছে, কোনও এক কালে আনন্দবাজারের ভূমিকা ছিল মুসলমানবিরোধী, সেই কোনও কালে আমার জন্মও সম্ভবত হয়নি, আমি এর দায় নিই কী করে! সম্পাদক বদলায়, প্রকাশক বদলায়, নতুন নতুন সাংবাদিক যোগ হন, পত্রিকার চরিত্র আদর্শও সেই সঙ্গে বদলায়। বাংলাদেশে যে পত্রিকা এক সময় দেশ স্বাধীনের বিরুদ্ধে লিখত, সেই পত্রিকাই এখন পক্ষে লিখছে, এর কারণ পুরোনো কালের মানুষ সরে গিয়ে নতুন কালের মানুষ এসেছে পত্রিকায়, পত্রিকার নাম ঠিকানা একই আছে, কিন্তু লেখা আগের চেয়ে আলাদা, মূল্যবোধ ভিন্ন। দ্বিতীয় অভিযোগটি হল আমি র এর এজেন্ট। গুজবের মত সংক্রামক আর কিছু নেই বোধহয়। ইনকিলাব আজ লিখল আমি র এর এজেন্ট, পরদিন দশটি পত্রিকায় লিখে ফেলে আমি র এর এজেন্ট।
রি কি?’ এই প্রশ্নটি মনে উঁকি দেয়। মিলনের কাছে জিজ্ঞেস করি, ‘মিলন র কি?’
মিলন বলে, ‘বুবু আপনে র মানে কি বুঝেন না! র তো হইল .. ‘
‘র তো হইল কি?’
‘মানে ধরেন র চা। দুধ না মিশাইয়া চা বানাইলে তো র চা -ই হয়। ধরেন আমগর কম্পানিতে র মাল আমদানি করে, পরে এই র মাল গুলা দিয়া প্রসেস কইরা কেমিকেল প্রডাক্ট বানানি হয়।’
‘কিন্তু র এর এজেন্ট মানে কি?’
‘মনে হয় বিদেশ থেইকা র মাল টাল আনার এজেন্ট।’
‘কিন্তু আমি তো কোনও র মাল আনার এজেন্ট না!’
‘লেখছে আর কী! আপনেরে নিয়া আজাইরা কত কথাই ত লেকতাছে ওরা।’
‘কিন্তু মিলনরে এর এজেন্ট বইলা আমারে গালি দিব কেন? মানুষ তো বিদেশি কত জিনিস পত্র আনে, তারা ত গালি খায় না!’
‘দিছে আপনেরে গালি। মনে করছে নিষিদ্ধ কোনও র মাল আনেন।’
‘নিষিদ্ধ মাল?’
‘এইটা বুঝেন না বুবু!’ মিলন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে। ‘বাংলাদেশে কি বিদেশের সব র মাল আসা লিগাল নাকি? কিছু ত নিষিদ্ধ মাল আছেই!’
‘যেমন?’
‘ধরেন ফেনসিডিল, কাশির ওষুধ। ফেনসিডিল খাইয়া পুলাপান নেশা করে। ইণ্ডিয়া থেইকা ফেনসিডিল আনে চুরাকারবারিরা। এহন যদি আপনি ফেনসিডিল আনেন, তাইলে কি তা নিষিদ্ধ না?’
‘কিন্তু ফেনসিডিল তো কোনও র জিনিস না। ওষুধ। বোতলের ওষুধ।’
‘ওই ফেনসিডিল বানানির মাল যদি আনেন হেইডা ত র ই। ঘরে বইয়া বানাইলেন।’
‘তাইলে আমারে চুরাকারবারি বা ইললিগাল ব্যবসায়ী কইতে পারত। র এর এজেন্ট কয় কেন?’
‘মনে করছে আপনের কোনও গ্রুপ আছে। গ্রুপটা র মাল আনে। আপনে জড়িত আছেন গ্রুপ এর সাথে।’
‘কিন্তু আমি ত এইরকম কোনও গ্রুপের সাথে জড়িত না।’
‘জড়িত থাকতে হইব নাকি! ওরা আপনের বিরুদ্ধে লিখতে চায়। এহন যেইডা লিখলে জনগণের মন আপনের দিকে বিষাক্ত হইয়া উডে, সেইডা লিখতাছে।’
মন থেকে র যায় না। র এর এজেন্ট আমি। আমার সঙ্গে যাদের ওঠা বসা, তারা কেউ এ ধরণের ব্যবসা করে না। তবে কেন আমাকে র এর এজেন্ট বলবে! অনেকদিন আমি মীমাংসাহীন র র মন নিয়ে বিষণ্ন বসে থাকি। মাস গেলে পর একদিন খসরু এলে তাকেই জিজ্ঞেস করি, ‘আচ্ছ! খসরু ভাাই, র কি?’ খসরুর সঙ্গে আমার পরিচয় শিপ্রার মাধ্যমে। লোকটি ব্যবসায়ী, দুটো ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু নিয়ে এনার্জি প্যাক নামে একটি জেনারেটর তৈরির কারখানা দিয়েছে। মতিঝিলে অফিস। প্রায়ই আমার বাড়িতে আসেন। কেমন আছি না আছি জানতে চান।
রি মানে? কি ব্যাপারে র?’ খসরু জানতে চান।
‘আমারে বলে আমি নাকি র এর এজেন্ট।’
খসরু অট্টহাসি হাসেন।
‘তোমারে র এর এজেন্ট বলতাছে, আর তুমি নিজে জানো না র কি? এইটা কোনও কথা হইল?’
মিলনের সংজ্ঞাটি গলগল করে মুখে এসে যায়। তার আগেই খসরু বলেন, ‘র হইল ইন্ডিয়ার ইণ্টেলিজেন্স এজেন্সি ! আমেরিকার যেমন সিআইএ। ভারতের তেমন র।’
আমি তাজ্জব হয়ে বসে থাকি। ‘তাই নাকি!’
‘তুমি নিশ্চয়ই জানো।’
‘না আমি জানতাম না।’
‘বল কি? তোমার পেছনে যে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক ঘুরে, তা জানো? তুমি যেইখানে যাও, তোমারে ফলো করে।’
‘নাহ! ক্ই। আমি তো দেখি নাই! মানে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ! কন কি!’
‘দেখ গিয়া বাড়ির সামনে একজন হাঁটতেছে। তোমার বাসায় কে আসতেছে, বাসা থেকে কে কোথায় যাচ্ছে, সব খবর রাখতেছে।’
আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কি অন্যায় করেছি আমি যে আমাকে র এর এজেন্ট বলবে। পুলিশের গোয়েন্দা বাহিনী আমার পেছনে লেগে থাকবে! অন্যায়টি খুঁজতে থাকি। অন্যায় খুঁজে পাই না। এ দেশের রাজনীতি হয় ভারত বিদ্বেষ দিয়ে, যে যত বেশি ভারত বিদ্বেষ দেখাতে পারবে, সে তত ভোট পাবে। দেশের মানুষের কথা ভাবার জন্য রাজনীতিবিদ নেই বললেই চলে। আমার পেছনে যে চর লাগা, তা ভারতীয় দূতাবাসের এক অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময়ই লক্ষ করি। একটি সাদা গাড়ি আমার রিক্সার পেছন পেছন সারা পথ গেল। আমার গতিবিধি সরকারি নথিভুক্ত হচ্ছে। আমি শান্তিনগর বাজারে গিয়ে ফুলকপি আর পুঁটিমাছ কিনলেও পেছনে সরকারি বাহিনী যাবে। ঘাড়ের কাছে আমি টের পাই কারও কারও নিঃশ্বাস। আমার ভয় হতে নিয়েও হয় না। আমি জানি আমি কোনও মূল্যবান মানুষ নই। ডাক্তারি করি, অবসরে লিখি। এমন কোনও ডাক্তারি নয়, এমন কোনও লেখা নয়। ভাল ডাক্তার হতে গেলে এফসিপিএস পাশ করতে হয়। ভাল লেখক হতে গেলে বাংলা সাহিত্যে অঢেল জ্ঞান থাকা চাই। আমার এফসিপিএসও হয়নি। সাহিত্যের অঢেল জ্ঞানও নেই।
বিচিন্তা পত্রিকাটি ফলাও করে ছেপেছে সুকুমারী থেকে চুরি। আমার বইয়ের লেখাগুলো আমার নয়, অন্যের। সুকুমারী থেকে চুরির জন্য যে শাস্তি আমার পাওনা, সে আমি মাথা পেতে গ্রহণ করতে রাজি আছি। কিন্তু চুরি বিশারদরা বলতে শুরু করেছেন নির্বাচিত কলাম বইটিতে ইসলামকে গাল দিয়েছি আমি, পুরস্কার পাওয়া তো আমার উচিত হয়ইনি, আমার শাস্তি পাওয়া উচিত। যে লেখা আমার নয়, অন্যের, সে লেখার জন্য আমি শাস্তি পেতে যাবো কেন! কিন্তু শাস্তির দাবি তারা করে এবং তখন কিন্তু একটুও অনুমান করে না যে যেসব লেখার কারণে তারা আমার শাস্তি দাবি করছে, সেসব আমার নিজের না হয়ে অন্যের হতে পারে। আমার শাস্তির দাবি না করে তো সেই অন্যের শাস্তির দাবি তাদের করা উচিত! কিন্তু না, তারা আমাকেই শাস্তি দেবে। গ্লানির গভীরে ডুবে থাকা আমাকে কে যেন ডেকে তোলে। কে যেন আমার কানে কানে বলতে থাকে, বেদ সম্পর্কে মন্তব্য তোমার নিজের না হলেও ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য তো তোমার নিজের! মূলত বইটি কি বেদ নিয়ে, নাকি মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থা নিয়ে লেখা? আমি ক্লান্ত কণ্ঠে বলি, লেখাগুলো তো আমার এবং আমার চারপাশের জীবনের কথা। কানে কানের কেউ বলে, শাস্তি সে কারণে তোমাকেই দিতে চাইছে, সুকুমারীকে নয়। যদিও ডাক শুনে উঠেছি, আমার বিস্মিত চোখ লক্ষ করে আমার আগের উচ্ছঅল উজ্জ্বল পরিবেশটি কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে। আগে যারা আমার লেখা নিয়ে বলত যে আমি ভাল লিখছি, চমৎকার লিখছি, তারাই এখন দোষ ত্রুটি ধরছে আমার লেখায়। দোষ ত্রুটি ধরছে কারণ আমি পুরস্কার পেয়েছি। পুরস্কার পাওয়ার লেখকের লেখার মান যে উঁচুতে থাকে, সেই উঁচুতে আদৌ আমার লেখা আছে কি না তা তারা বিচার করে দেখছে। বিচারে হার হচ্ছে আমার। আনন্দ পুরস্কার আমাকে একটি অদ্ভুত অচেনা জগতে টুপ করে ফেলে দিয়েছে। বড় একা লাগে নিজেকে। যেন একটি সিন্দুকের ভেতর আমাকে আর আনন্দ পুরস্কারটিকে পুরে সিন্দুকটি বন্ধ করে দিয়েছে কেউ, আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকে।
কলকাতায় যখন আমাকে নিয়ে উচ্ছঅ!স খুব প্রচণ্ড, নির্বাচিত কলাম বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে আশাতীত রকম বিক্রি হতে শুরু করেছে। তখনই খবর বেরোলো যে আমি চুরি করে বই লিখেছি। চৌর্যবৃত্তির খবর এক দেশ থেকে ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে আরেক দেশে খুব দ্রুত চলে যায়। বিচিন্তার খবর হুবুহু ছাপা হয়ে যায় কলকাতার পত্রিকায়। আনন্দবাজার বিরোধী পত্রিকাগুলোর জন্য এ চমৎকার এক খবর বটে।সুকুমারী থেকে চুরি নিয়ে কলকাতায় খুব বেশি না হলেও কিছু কাণ্ড ঘটে গেছে। নারীবাদী লেখিকা মৈত্রেয়ী চট্টে াপাধ্যায় আমার এই চুরি নিয়ে মুখর হয়ে উঠলেন। কেন আমি চুরি করতে গেলাম, কেন তথ্য স্বীকার করিনি সুকুমারীর বইয়ের সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পণ্ডিত শিব নারায়ণ রায় মৈত্রেয়ীর প্রতিবাদ করে লিখলেন, দৈনিক পত্রিকার কলামে তথ্য স্বীকারের প্রয়োজন হয় না, হত গবেষণামূলক কোনও গ্রন্থ, কথা ছিল। শিব নারায়ণ রায় আনন্দ বাজার পত্রিকায় বড় একটি লেখাও লিখলেন, মিথ্যে কলংক রটিয়ে এই তীক্ষ্ণ কলমকে ভোঁতা করা যাবে না। কলকাতায় না হয় একটি রফা হল। কিন্তু বাংলাদেশে চোর চোর বলে কিছুদিন গালাগাল করে বইয়ের কোথায় কোথায় কোরান হাদিস সম্পর্কে আমি কী বলেছি তা নিয়ে পড়ল। মামলা ঠুকে দিল আমার বইয়ের প্রকাশকদের বিরুদ্ধে। যেসব পত্রিকায় লিখি, সেসব পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশকদের বিরুদ্ধেও মামলা। প্রকাশ্যে বই পোড়ানো হল। বইয়ের দোকানগুলোয় হুমকি দিয়ে এল আমার বই বিক্রি করলে মাথা ফাটিয়ে দেবে। ইনকিলাব পত্রিকায় একজন লিখলেন, আমার ফাঁসি হওয়া উচিত। ফাঁসি! এ আর এমন কী নতুন দাবি! সাধারণত রাজনৈতিক জঙ্গী মিছিলে অসৎ রাজনৈতিক নেতাদের ফাঁসি চাওয়া হয়। ফাঁসি তো আর সত্যিকার হয় না। মনের রাগ প্রকাশ ফাঁসি চাই বলেই প্রকাশ করার অভ্যেস মানুষের।— প্রবোধ দিই নিজেকে। কিন্তু কোথায় যেন কিসের একটা কাঁটা বিঁধে থাকে।
নারীর ওপর নির্যাতন নিয়ে লিখছিলাম, লোকে বাহবা দিচ্ছিল। কিন্তু যখনই নারীর ওপর নির্যাতন কেন হয়, তা তলিয়ে দেখতে গিয়ে ধর্মের কথা বলেছি, তখন দেখি আমি আর বাহবা পাচ্ছি না। মৌলবাদিদের কথা বলছি না, যাঁরা পাঁচ বেলা নামাজ পড়েন না, রোজা করেন না, দাড়ি কামিয়ে, সুটেড বুটেড হয়ে নিজেদের প্রগ্রেসিভ আখ্যা দিয়ে ঘুরে বেড়ান, যে মেয়েরা বেআব্রু চলাফেরা করেন, পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশাও করেন অনায়াসে, গানবাজনা কালচার ইত্যাদি নিয়ে আছেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা, যে মেয়েরা নারীমুক্তির আন্দোলন করছেন যুগ যুগ ধরে, সংস্থা খুলেছেন, সমিতি বানিয়েছেন, তাঁরাও ভুরু কপালে তুলে বলেন, ‘মেয়ের সাহস কত দেখ! ধর্মের বদনাম করছে। মৌলবাদিদের কার্যকলাপ নিয়ে লিখছিল, সে না হয় ভাল, কিন্তু ধর্মকে টানা কেন! ধর্ম দোষটা কি করেছে!’ আমার সমর্থকরাও আমার বিরোধী হয়ে উঠল। কোনও ধর্ম বিশ্বাসের বালাই যেন যাঁদের, নারী পুরুষের সমতায় যাঁরা বিশ্বাস করেন, কেবল বিশ্বাস করলেই হয় না, যাঁরা সংষ্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক—তাঁরাই কেবল আমাকে সমর্থন করছেন। অবশ্য সকলে নয়। আহমদ ছফা, লেখক বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি নানা নামে ভুষিত তিনি, দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছেন আমার বদনাম করার জন্য। কাগজে নিরবধি লিখে যাচ্ছেন আমার বিরুদ্ধে। আহমদ ছফাকে আমি রুদ্রর মাধ্যমে চিনি, রুদ্র বেশ ভক্ত ছিল ছফার। ছফা দেখতে অনেকটা মামদো ভুতের মত। মামদো ভুত আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু ছোটবেলায় মামদোভুতের গল্প যখন শুনতাম, ঠিক এরকম একটি মানুষের মত দেখতে অথচ মানুষ নয় কিছুর আমি অনুমান করতাম। প্রথম যেদিন আমি ছফাকে দেখি, সেদিনই রুদ্রকে বলেছিলাম, তোমার এই ছফা ভাই দেখতে এমন কেন? দেখতে কেমন? রুদ্র বলেছিল। বলেছিলাম, দেখতে কেমন যেন মামদো ভুতের মত। রুদ্র আমার এই বেফাঁস মন্তব্যের উত্তরে বলেছে, ছফার মত জ্ঞানী লোক খুব কমই আছেন এ দেশে। ছফার প্রতি রুদ্রর শ্রদ্ধার একটি কারণ ছিল, রুদ্রর প্রথম বই ছাপতে ছফা সাহায্য করেছিলেন। রুদ্র ছফাভক্ত, ছফা যেমনই দেখতে হোক না কেন। ছফা লিবিয়ার টাকা খেয়ে ইসলাম ইসলাম জপ করছেন বলে বাজারে গুঞ্জন ছিল। রুদ্র ওসব কথায় কান দেয়নি। আমাদের রাজাবাজারের বাড়িতে ছফা এসেছেন দুদিন, রাতে থেকেওছেন। বিকট সুরে যখন এক রাতে গান গাইতে শুরু করলেন, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভয় পেলেও ভক্তি জিনিসটি সংক্রামক। রুদ্রর ছফাভক্তি আমার ভেতরেও খুব দ্রুত ছড়িয়ে গেল। আমিও, যেমনই যেখতে হোন তিনি, তাঁকে ভক্তি করতে শুরু করলাম। কোনওকালেও বিয়ে না করা লোকটি নানারকম মেয়েদের নিয়ে গল্প করতেন। কলকাতার এক সুন্দরী মেয়ে ইন্দিরা ছফার প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছে, ছফা তাঁর মামদোভুতো মুখে প্রেমের সব বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করেন তাঁর ভক্ত শ্রোতার উপস্থিতিতে। পরে এই ইন্দিরাকেই একসময় বিয়ে করে নিয়ে আসেন মৃদুল চক্রবর্তী, ইত্যাদির আড্ডায় মাঝে মাঝে আসা গানের ছেলে মৃদুল। কেবল গানের ছেলেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেও বটে, মাস্টারি করেন। ছফার সঙ্গে বিভিন্ন দূতাবাসের মাখামাখি আছে, বিশেষ করে জার্মান দূতাবাসের। গ্যাটের ফাউস্ট বইটি অনুবাদ করে ফেললেন একদিন। রুদ্রর সঙ্গে বিচ্ছেদের পরও আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে ছফার দেখা হত। দেখা হত মূলত ইত্যাদিতে। একসময় আমার কবিতা অনুবাদ শুরু করলেন তিনি। আমাকে তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্নও করেছেন। ফাউস্টের অনুবাদক করছেন আমার কবিতার অনুবাদ! কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করে আমাকে রীতিমত ভয় পাইয়ে দেন ছফা। এমন কবিতা নাকি লেখা হয়নি বাংলা সাহিত্যে। আমার কবিতা সারা বিশ্বে অনুবাদ হওয়া উচিত। তাঁর ইচ্ছে আমার কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদের বই তিনি ছাপবেন। এমন যাঁর আবেগ তিনি কি করে এমন হঠাৎ বদলে গেলেন, সুনামের সমুদ্র থেকে বদনামের বিলে ঝাঁপ দিলেন! এটি একটি প্রশ্ন বটে। আমি আনন্দ পুরষ্কার পেলাম, তাতে তাঁর এত মনোকষ্ট হওয়ার কারণ কি! ছফাকে একদিন আমি আমার আরমানিটোলার বাড়িতে রাতের খাবারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে দেখি লিলি নেই। দরজা হাঁ হয়ে আছে, ভেতরে সব আছে, কেবল তিন ফুট তিন ইঞ্চি, গোলগাল মুখ, গায়ের রং কালো, পরনে সবুজ হাফপ্যান্ট, লাল জামাটি নেই। নেই তো নেই, কোথাও নেই। দক্ষিণা হাওয়ায় কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে। পাতিপাতি করে পাড়া খুঁজে, আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ি খুঁজে, রাস্তাঘাটনদীরপাড় খুঁজে থানায় ডায়রি করে রাতে যখন বাড়ি ফিরলাম, এর মধ্যে দুঘন্টা দারোয়ানের ঘরে বসে অপেক্ষা করে চলে গেছেন আহমদ ছফা। সে রাতে অবশ্য আরমানিটোলার রাস্তায় উদাসীন দাঁড়িয়ে থাকা লিলিকে পাওয়া যায়। আহমদ ছফার কাছে সেদিনের ঘটনাটি বলব, ক্ষমা চাইব, তার আগেই তিনি পত্রিকায় লিখে ফেললেন আমার নিন্দা করে একটি কলাম। আনন্দ পুরষ্কার পাওয়ার পর নিন্দা লাগামছাড়া হয়ে উঠল। আনন্দবাজার আর দেশ থেকে প্রথম বাংলা একাডেমিকে পুরষ্কার দিতে চেয়েছিল, বাংলা একাডেমি সে পুরষ্কার নেবে না জানিয়ে দিয়েছিল। এরপর আমাকে যখন নির্বাচন করা হল পুরষ্কারের জন্য, আহমদ ছফা লিখলেন, ‘আসলে তসলিমা নাসরিন কিছুই না। সবটাই ছ্যাবলামো আর চৌর্যবৃত্তিতে ভরপুর। যেহেতু সে মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে লিখেছে সে জন্যে আনন্দবাজার তাকে লাইম লাইটে নিয়ে এসেছে।.. গ্রামের দুই মাতবর প্রতিবছর একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়ায়। একবার হল কি, এক মাতবর প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য বাড়ির কাজের মেয়েটিকে অন্য মাতবরের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আনন্দবাজারের কর্মটিকে আমার সেরকম মনে হয়েছিল। যেহেতু বাংলা একাডেমি পুরষ্কারটি প্রত্যাখ্যান করল, সেজন্য ক্ষুব্ধ ব্যথিত হয়ে বাংলা একাডেমির মুখে একটি চপেটাঘাত করার জন্য তাঁরা তসলিমাকে বেছে নিলেন।’
কী ছফা কী হয়ে গেলেন! পত্রিকায় তসলিমাবিরোধী কলাম লিখে আহমদ ছফার শান্তি হল না, পুরো একটি বই লিখে ফেললেন তিনি। আহমদ ছফার লেখার প্রতিবাদ করে একদিন বিরুপাক্ষ পাল লিখলেন একটি কলাম। ‘আহমদ ছফার মত প্রাজ্ঞ সাহিত্যিকের দ্বারা এ ধরনের রূপকের ব্যবহার তাঁর ধৈর্যচ্যূতি ও ঈর্ষামূলক ক্ষোভকে প্রকট করে তুলেছে সর্বসমক্ষে। যৌবনে পুরষ্কৃত বা নন্দিত হওয়ার বিপদ অনেক, কিন্তু এ ধরনের অপবাদমূলক বিপদের জন্য বোধহয় কেউ বোধহয় প্রস্তুত থাকেন না। পুরষ্কার উত্তর পর্বে তসলিমা সংবাদপত্রে অনেক কথা বলেছেন। আহমদ ছফার মতে—আমি মনে করি না তসলিমা এসব কথাবার্তায় যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিতে পেরেছেন। শুধু তসলিমার দোষ দিয়ে লাভ কি! তথাকথিত অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই তো সংবাদপত্রের কলামে এন্তার আজেবাজে বকে থাকেন। ছফা সাহেব একটু ভেবে দেখবেন কি কথাগুলো তাঁর জন্যও প্রয়োগ করা যায়। তসলিমা নাসরিনের কথাবার্তায় আহমদ ছফা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পান না, তার কারণ হল, তসলিমা নাসরিন যা ভাবেন, সেটাই বলেন সাহসের সাথে। অন্য দশজন কচ্ছপসদৃশ বুদ্ধিজীবীর মতো তিনি তাল বুঝে মাথা বের করেন না, তিনি অনর্গল মাথা বের করেই আছেন। এ জন্যেই বোধহয় অনেক মৌসুমী সাহিত্যিকের মনে হয়, তাঁর কাণ্ডজ্ঞান কম। .’ কানে আসে নানারকম খবর। কবি রফিক আজাদ নাকি আমার মত তুচ্ছ লেখকের আনন্দ পাওয়ায় খুব ক্ষুব্ধ। রফিক আজাদ আমাকে খুব স্নেহ করতেন এরকমই আমার মনে হত। তাঁর প্রথম স্ত্রী আদিলা বকুল আমার কাছে মাঝে মধ্যে এসে মনের কথা বলে হালকা হন জেনে তিনি স্বস্তিবোধ করেছিলেন। আদিলা মেয়েটি বড় ভাল, অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন তাঁকে সঙ্গ দিই, মনের জোর দিই। আদিলা আমাকে তাঁর কষ্টের কথা অনেক বলেছেন। কবিতা লিখলে আদিলা বকুল রফিক আজাদের চেয়েও বড় কবি হতে পারতেন কিন্তু সরল সোজা সহিষ্ণু মানুষটি সারাজীবন কেবল দিয়েই গেছেন তাঁর স্বামীকে, নিজেকে নিঃস্ব করে একসময় দেখলেন স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। আদিলাকে তিনি ছেড়ে যান বা যাই করুন, এ কথা ঠিক যে রফিক আজাদ খুব বড় কবি। আমার মত ছোট কবি যদি ভুল করে একটি পুরস্কার পেয়েই যায়, তবে তো তাঁর বড়ত্ব কিছু কমে যায় না!
চারদিক থেকে মৌলবাদী আর দুর্মুখ লেখকদের বাক্যবাণে আমি যখন নাস্তানাবুদ তখন একদিন রফিক আজাদের চেয়ে অনেক বড়, আক্ষরিক অর্থে দেশের সবচেয়ে বড় কবি শামসুর রাহমান লিখলেন ‘তসলিমার কলমের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। লিখলেন,ইতিমধ্যে আমাদের সংষ্কৃতির ক্ষেত্রে তসলিমা নাসরিন একটি সাড়া জাগানো নাম। কলামিস্ট হিসেবে তিনি বিখ্যাত, তাঁর খ্যাতি দেশের সীমানা অতিক্রম করেছে। কলামের জন্য তিনি পুরষ্কৃত হয়েছেন বিদেশে। তিনি অনেক প্রথাবিরোধী কথা বলেছেন, তাঁর কলামগুলো সাহসী উচ্চারণে ভরপুর। তসলিমা নাসরিনের সাহসের তারিফ করতে হয়। তিনি আমাদের পুরুষশাসিত,পশ্চাৎপদ, ঘুণেধরা সমাজকে চাবকেছেন বার বার, অচলায়তনকে দিয়েছেন ধাককা। ধর্মীয় গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে ঠোঁটকাটা মন্তব্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। কোনো রাখঢাক নেই তাঁর উচ্চারণে। কবুল করতে দ্বিধা নেই, আমি অন্তত তসলিমা নাসরিনের মত সাহসী নই। আমার এমন অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হয় যা আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি, কিন্তু জন্মান্ধ সমাজপতি এবং তিমিরবিলাসী, মধ্যযুগে বসবাসকারী ঘাতকদের ভয়ে সেসব কথা বলা থেকে বিরত থাকি। এতে আমার ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হয়, নিজের অক্ষমতার জন্য লজ্জাবোধ করি আর তসলিমা নাসরিনকে মনে মনে সাধুবাদ জানাই।’
কবিতার বইগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের সমাজের অনেকেই নারীর ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত হতে দিতে চায় না। চারদিক থেকে নিষেধের তর্জনী এবং ছিঃ ছিঃ রব ওঠে। নারী যে একজন মানুষ, এই বোধ জাগ্রত নেই সমাজের মনে। এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেন না বলেই তসলিমা দ্রোহী হয়ে ওঠেন, নিজের পায়ের বেড়ি ভেঙে ফেলেন, অন্যদেরও ভেঙে ফেলার আহবান জানান।’
কেবল শামসুর রাহমান নন, এপার বাংলার জাহানারা ইমাম, রশীদ করীম, নাজিম মাহমুদ, মযহারুল ইসলামের মত বিদগ্ধ ব্যক্তি লিখেছেন আমাকে নিয়ে। ওপার বাংলার শঙ্খ ঘোষ, ভবতোষ দত্ত, কেতকি কুশারি ডাইসন, শিব নারায়ণ রায়, আনন্দ বাগচি, মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, সুতপা ভট্রাচার্যের মত বড় বড় লেখক ওখানকার কাগজে আমার লেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেউ বলছেন দুর্দান্ত, কেউ বলছেন দুঃসাহসী, দুর্বিনীত, এমন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বড় দুস্প্রাপ্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা লিখেছেন, ‘তসলিমা নাসরিন আজ আমাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক। তাঁর নির্বাচিত কলাম এই মুহূর্তে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই, সমাজের পাইক পেয়াদা ঠেঙারে বরকন্দাজদের গাঁজলা ওঠা হল্লারও প্রধান কারণ এই বই।’ —এ সবই অপ্রত্যাশিত। আমার জন্য অতিপ্রাপ্তি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনন আবৃত্তি সংঘ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। স্বননের সঙ্গে জড়িত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেখক বুদ্ধিজীবিদের তালিকায় সনৎ কুমার সাহা একজন। আমাকে স্বম্বর্ধনা দেওয়া হয় স্বননের পক্ষ থেকে। বিখ্যাত লেখক হাসান আজিজুল হক আমাকে ফুলের তোড়া দিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানান, আমার সম্পর্কে স্তূতিবাক্য আওড়ান। আমি তো মঞ্চে বসে স্তূতির তোড়ে ভেসে যেতে থাকি। আমাকে যখন বলতে বলা হল, দুটো কী একটি ধন্যবাদ জাতীয় বাক্য বলার পর দেখি মাথা ফাঁকা। ফাঁকা মাথা থেকে আর কোনও শব্দ আমার জিভের দিকে আসছে না। সাহিত্য সংস্কৃতি যেমন আসে না, রাজনীতি, সমাজ ইত্যাদিও আসে না। জানি শ্রোতারা অপেক্ষা করছেন কড়া কড়া কিছু কথা শোনার জন্য কিন্তু সকলকে হতাশ করে আমাকে বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কিন্তু কবিতা যেদিন পড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে, সাবাস বাংলাদেশ নামের বিশাল মুক্তিযোদ্ধা-মূর্তির সামনে, আমার কণ্ঠে কোনও জড়তা ছিল না। কবিতা পড়তে দাও, সারারাত ক্লান্তিহীন পড়ে যাবো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই, আবার ইসলামী ছাত্র শিবিরেরও অভাব নেই। শিবিরের পাণ্ডারা প্রগতিশীল ছাত্র শিক্ষকদের দিব্যি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করছে, হাত পায়ের রগ কেটে দিচ্ছে। হিশহিশ শব্দ সারাক্ষণ ঘাড়ের পেছনে, আশঙ্কারা ঘাপটি মেরে বসে থাকে লোমকূপে। সনৎ কুমারই লিখেছেন, যখন আমি কবিতা পড়তে মঞ্চে উঠেছি, ‘কবিতা শোনার আগ্রহের সঙ্গে মেশে এক অরুচিকর অস্থিরতা, আজকের বাংলাদেশে যার পৌনঃপুনিক আক্রমণে আমরা এখন প্রায় অভ্যস্ত। বুকের ভেতর শুনতে পাই চাপা ধুকপুকুনি, যেন বিশ্রী একটা কিছু ঘটে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। .. পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি শ্রোতাদের ভেতর কোনও কোনও অংশে মূর্তিমান বীভৎসতা থোকায় থোকায় কুণ্ডুলি পাকিয়ে তার সমস্ত কদর্যতা উগরে দিতে চাইছে। সেখানে হামলে পড়া মুখগুলো থেকে জান্তব লালসার লাম্পট্য গলে পড়তে থাকে। চোখের তারায় ফিনকি ছোটে ঘৃণার আর প্রত্যাখ্যানের। যেন এক মূর্তিমান আপত্তিকে হিংস্র আক্রমণে ছিন্নভিন্ন করতে পারলেই তাদের নিশ্চিন্তি।’ নাহ, ছিন্নভিন্ন আমাকে হতে হয়নি। কবিতা পড়ে আস্ত আমি মঞ্চ থেকে নেমেছি[ রাজশাহীতে নাজিম মাহমুদের বাড়িতে ছিলাম, যে কদিন ছিলাম। খুব প্রাণোচ্ছল মানুষ নাজিম মাহমুদ, আমাকে নিয়ে, আমার লেখা নিয়ে উচ্ছ!সের তাঁর শেষ নেই। এমনিতেও হৈহুল্লোড় করা মানুষ তিনি। কিছু কিছু মানুষের বয়স হয় না। কিছু কিছু মানুষ সজীব কিশোর থেকে যেতে পারেন বৃদ্ধ বয়সেও। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে দেখালেন আমাকে। অনেকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে নিলেন। অভিনন্দনের ঢল নামে কিন্তু এতেও তুষ্ট হন না সনৎ। লেখেন, ‘যে সুস্থতার স্বপ্ন তসলিমার চোখে, যার জন্যে আমাদের সবার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তাকে আমরা প্রাণ খুলে অভিনন্দন জানাতে পারি না। মলিন মুখে কুণ্ঠিত হাত তুলে চুপিচুপি সহমর্মিতা আর একাত্মতা জানিয়ে বিদায় হই। বুঝতে পারি, এর বেশি এগুনো যাবে না।’ আমার কিন্তু মোটেও মনে হয়নি আমাকে কিছু কম ভালবাসা হচ্ছে। বরং বার বারই বলেছি মনে মনে, এত আমার কাম্য ছিল না তো! এটা ঠিক যে আমাকে যখন ঝেড়ে গাল দেওয়া হয়, আমি অনেকটা প্রস্তুত থাকি গাল খাবার জন্য, যেন এই গালই আমার প্রাপ্য ছিল। কেউ প্রশংসা করলেই চমকে উঠি, বুকের ভেতর কেমন জানি লাগে। আমি বুঝি যে প্রশংসা আমাকে লজ্জা দিচ্ছে, কুণ্ঠা দিচ্ছে, অস্বস্তি দিচ্ছে। প্রশংসা পাওয়ার জন্য মনে মনেও প্রস্তুত থাকি না।
লেখালেখি চলছে। পক্ষে বিপক্ষে। তবে পক্ষের লেখার তুলনায় বিপক্ষের লেখাই বেশি, বিপক্ষের কলমে ধার বেশি, তেজ বেশি, ক্ষোভ বেশি। আমার নামের সামনে থেকে, লক্ষ্য করি, জনপ্রিয় শব্দটি তুলে দিয়ে বিতর্কিত শব্দটি বসানো হচ্ছে। আমার লেখা নিয়ে বিতর্ক হয়, এত বিতর্ক নাকি অন্য কোনও লেখক নিয়ে হয় না। আমি যা-ই লিখি না কেন, লেখাগুলো মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, ভাবায়, রাগায়, কিছু না কিছু করেই। লেখাগুলো নিয়ে কেউ না কেউ কিছু বলেই। লেখার সীমানা ছাড়িয়ে আমার শরীরের দিকে ধেয়ে আসে অনেকের লম্বা লম্বা জিভ, ধার ধার নখ। বাংলার বাণী পত্রিকায় মীর নূরুল ইসলাম আমার প্রসঙ্গে লিখেছেন ভিন্ন দৃষ্টির অন্যরকম একজন কবি শিরোনাম দিয়ে একটি কলাম। ‘যাঁকে নিয়ে এত কথা, তাঁকে আমি কখনো দেখিনি। তাঁর বিপক্ষে শুনেছি অনেক অশ্রাব্য কথা। সেসব কথায় শ্লেষ আছে, বিদ্রুপের বিষাক্ত বাক্যবাণ আছে। শুধু নেই কাব্য প্রতিভার আলোচনা কিংবা সমালোচনা। শারীরিক তত্ত্ব ও তথ্যের কথা বলা হয় মজাদার মশলার মিশ্রণে। যেন একটা নারীদেহ কেটে হাঁড়িকাবাব বা বটিকাবাব বানিয়ে মাংসলোভীদের সাজানো টেবিলে পরিবেশন করা হল। অথচ এই মানসিকতার বিরুদ্ধেই তিনি সোচ্চারকণ্ঠ। এই হিংস্রতা আর পাশবিকতার বিরুদ্ধেই প্রতিপক্ষকে জাগ্রত করার দুর্বার সাধনায় পরিচালিত তাঁর কালি কলম।’
পক্ষের লেখাগুলো চেয়ে বিপক্ষের লেখাগুলো আমি মন দিয়ে পড়ি। দৈনিক সংগ্রাম, ইনকিলাব, দিনকাল, মিল্লাত, বাংলাবাজার পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে। সংগ্রাম, ইনকিলাব, মিল্লাত মৌলবাদিদের পত্রিকা। বাংলাবাজার পত্রিকার প্রকাশক সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরি যদিও মৌলবাদী নন, কিন্তু আমার প্রসঙ্গ এলে মৌলবাদীদের পক্ষ নিতে দ্বিধা করেন না। মতিউর রহমান চৌধুরির সঙ্গে আমার কখনও কোনও বিরোধ ছিল না, বিরোধ শুরু হল যখন তিনি কলকাতার দেশ পত্রিকা বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। দেশে নীরদ চৌধুরীর একটি লেখা ছিল যেখানে তিনি বাংলাদেশকে তথাকথিত বাংলাদেশ বলেছেন। নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে কয়েক বছর পর এ নিয়ে কথা হয়েছে আমার, আমি যখন জিজ্ঞেস করেছি কেন তিনি বাংলাদেশকে তথাকথিত বাংলাদেশ বলেছেন, তিনি উত্তরে, হেসে, বলেছেন, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বাংলা অঞ্চল মিলিয়ে বংলাদেশ। পূর্ববঙ্গের কোনও অধিকার নেই বাংলাদেশ নামটিকে দখল করার। পশ্চিমবঙ্গ আজও পশ্চিমবঙ্গ রয়ে গেছে। নীরদ চৌধুরীর যুক্তি আমি শুনেছি। যে যুক্তি মতিউর রহমান চৌধুরি দিয়েছিলেন, তাও শুনেছি। মতিউরের বক্তব্য তথাকথিত বাংলাদেশ বলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। তা মেনেছিলাম। কিন্তু তারপর যে কাণ্ডটি তিনি করতে শুরু করলেন, তা মানতে পারিনি। কলকাতা থেকে বাংলাদেশে দেশ আসা চিরকালের জন্য বন্ধ করতে হবে, এই দাবি নিয়ে তুমুল হৈ চৈ শুরু করলেন। দেশ পত্রিকার প্রকাশক তথাকথিত শব্দটির জন্য ক্ষমা চাওয়ার পরও। সরকারের সঙ্গে মতিউরের মাখামাখি থাকার কারণে সরকার থেকে হঠাৎ একদিন দেশ পত্রিকার সবগুলো কপি বাজেয়াপ্ত করা হল, বাংলাদেশে দেশ আসা বন্ধও করে দেওয়া হল। দেশের পাঠকেরা মুখ চুন করে বসে রইল। দেশ উন্নত মানের সাহিত্য পত্রিকা। এটি বন্ধ হওয়ার পর প্রতি সপ্তাহে আমাদের পড়ার মত তেমন কোনও কাগজ রইল না। বাংলা ভাগ হয়ে গেছে, এ দেশের রাজনীতি এখন ভারত বিরোধী রাজনীতি, যে যত বেশি ভারতকে গাল দিতে পারে, তার তত জনপ্রিয়তা বাড়ে। এক দল অন্য দলকে দোষ দিয়ে যাচ্ছে, অন্য দল নাকি ভারতের কাছে এ দেশটি বিক্রি করে দেবে। প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে এরকম লাগাতার লেগে থাকলে এ দেশের কি সত্যিকার কোনও লাভ হয়! কোথায় ভারত, কোথায় বাংলাদেশ। হাতির সঙ্গে মশা লেগেছে ঝগড়া করতে। দুই বাংলা মিলে যদি না যেতে পারে না যাক, অন্তত সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগটি তো থাকতে পারে। এতে দুই বাংলার মানুষেরই তো উপকার হয়! তথাকথিত শব্দের তথাকথিত অপরাধে দেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেলে এ দেশের কার কতটা কী অর্জন করা হয় বুঝতে পারি না। দেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় এমনই রাগ হয়েছিল যে প্রতিবাদ করে একটি কলাম লিখলাম পত্রিকায়। দেশের বিরুদ্ধে মতিউর রহমানের এমন ক্ষিপ্ত হওয়ার মূল কারণটি কী তা উদ্ধার করে জানিয়ে দিলাম যে তিনি বাংলাবাজার পত্রিকায় শারদীয়া দেশের বিজ্ঞাপন চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেওয়া হয়নি বিজ্ঞাপন, দেওয়া হয়েছে ইত্তেফাক আর ইনকিলাবে, তাই তিনি আগুন হয়ে আছেন রাগে। মূল কারণ বিজ্ঞাপন, তথাকথিত শব্দটি কোনও কারণ নয়। আমার লেখাটি ছাপার পর মতিউউরের বিষধর ফণা আমার দিকে তাক করা। বাংলাবাজার পত্রিকাটিতে দিনে দুবার করে আমাকে কোপানো হয়। চরিত্র সামান্য পাল্টালো বাংলাবাজার পত্রিকার যখন মতিউর দেউলিয়া হয়ে পত্রিকা বিক্রি করে দিলেন ইয়াহিয়া খানের কাছে। মিনারের বদৌলতে সাহিত্য রসিক বস্ত্রকল ব্যবসায়ী ইয়াহিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আমার একটি হঠাৎ হঠাৎ দেখা সম্পর্ক রয়ে গেছে। ইয়াহিয়া আমার লেখার অনুরাগী তিনি। লেখার অনুরাগী হলে মাঝে মাঝে কেউ কেউ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন যে কোনও কাজে ব্যবহৃত হবার জন্য। আমার নিজের জন্য দরকার না হলেও নির্মলেন্দু গুণের জন্য বাংলাবাজার পত্রিকায় সাহিত্য সম্পাদক পদে একটি চাকরির জন্য ইয়াহিয়া খানকে ব্যবহার করেছি। পত্রিকাটির মালিক প্রকাশ্যে জাকারিয়া খান অপ্রকাশ্যে ইয়াহিয়া খান হলেও সম্পাদক তখনও মতিউর রহমান চৌধুরি। সম্পাদকের ঘরে বসে চা খেতে খেতে মতিউরের সঙ্গে গুণকে দুহাজার নয় তিন হাজার নয় পাঁচ হাজার টাকা মায়নের ব্যবস্থা পাকা করে তবে আমি কাপের শেষ চা টুকু তৃপ্তি করে পান করেছি। নির্মলেন্দু গুণের মত বড় কবিকে সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যপার। আমি কোনও অন্যায় আবদার করিনি। ইয়াহিয়া খানকে বলে তাঁর গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির শ্রমিকের কাজে গুণের পরিবারের সদস্য গীতার এক বোনকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, কিছু কাজের কাজ করে মনে প্রশান্তি আসে। ইসলামরক্ষকেরা ওদিকে একজন একজন করে লিখে যাচ্ছেন আমার বিরুদ্ধে। তবে তাঁরা যুক্তি খণ্ডনে না গিয়ে সোজা কোরান হাদিসের ধ্রুব সত্যকে সামনে খাড়া করেন। কোরান হাদিসের বক্তব্যে যুক্তি না থাকলেও আবু ফয়সল লিখলেন, ‘পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের ব্যতিক্রমী বিধানকে ভিত্তি করে নারীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা ব্যাখ্যা করা একাডেমিক অনেস্টি নয়। নাসরিন এই একাডেমিক ডিসঅনেস্টি প্রায় সবখানেই করেছেন। নাসরিন তাঁর লেখা দ্বারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তাঁর লেখা দ্বারা আলটিমেটলি ইসলামের কোনও ক্ষতিই হবে না। ইসলামের উপর এর চেয়ে অনেক ঘোরতর আক্রমণ যা বিভিন্ন কর্নার থেকে এসেছে যা ইসলামের পণ্ডিতগণ মোকাবিলা করেছেন এবং করতে সম্ভব।’ যদিও ইসলামের কোনও ক্ষতিই হবে না বলা হয়েছে, কিন্তু ইসলামপন্থীরা মোটেও আমাকে ভুলে থাকতে পারছে না, এমন ভাবে আক্রমণ করছে যেন আমি ইসলামের কল্লা কেটে ফেলে দিচ্ছি কোথাও। আমাকে রোধ করতে না পারলে, আশঙ্কা, ইসলাম নির্ঘাত মরবে।
ইনকিলাবে ছাপা হল ডাঃ গোলাম মোয়াযযমএর কোরআন পড়লে যাদের মাথা ঘোরে তাদের উদ্দেশে। লোকটি কোরানের যুগোপযোগী ব্যাখ্যায় বেশ ওস্তাদ। আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুর তথ্যই তিনি কোরআন ঘেঁটে বের করে দিতে পারেন। বিজ্ঞানে আজ নতুন কিছু আবিস্কার হল, কালই তিনি সেটি খুঁজে পাবেন কোরআনে। বলবেন, আল্লাহ তো এই তথ্য কবেই দিয়ে বসে আছেন। তবে মজার ব্যপার হল, বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের আগে কোরআনীয় আবিস্কারটি হয় না। বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাক হোলের কথা আগে বলেছেন, পরে কোরআনবিদরা ব্ল্যাক হোলের কথা খুঁজে পাবেন কোরানে। না পেলেও কোনও একটি আয়াতের ব্যাখ্যা এমন ভাবে করবেন যেন ব্ল্যাক হোলের কথাই আকারে ইঙ্গিতে আল্লাহ বলেছেন। কোরআনে লেখা আছে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, পাহাড়গুলো কিলক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে যেন পৃথিবী পড়ে না যায়। এতকাল এসব কথা মেনে এলেও এখন বিজ্ঞান-জানা মুসলমানরা স্বীকার করবেন না যে কোরআনে তা লেখা আছে। পরিস্কার আরবীর অপরিস্কার অনুবাদ করে বোঝাবেন, পৃথিবী স্থির বলতে আল্লাহ আসলে অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছেন। আল্লাহ কোথায় কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আল্লাহর চেয়ে আজকাল ধুরন্দর জ্ঞানীরা বেশি বোঝে। গোলাম মোয়াযযম লিখেছেন, ‘পৃথিবী স্থির এ কথা কোরআনে কখনও বলেনি। কোরআন বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক নয়। মানুষকে দ্বীন বোঝাবার জন্য আল্লাহ প্রাকৃতিক বহু বিষয়ের উদাহরণ দিয়েছেন এবং তাতে যা বলা হয়েছে সেগুলো বিজ্ঞানের সীমায় পড়ে। বাইবেল মানুষের লেখা বলে তাতে বহু বৈজ্ঞানিক ভুল তথ্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি মরিস বুকাইলি তার বিখ্যাত গ্রান্থে স্পষ্ট বলেছেন, কোরআনে কোনও ভুল তথ্য পাওয়া যায় না কারণ এটা মানুষের রচিত নয়। কোরআনে আছে আল্লাহর হুকুমে চন্দ্র সূর্য তাদের কক্ষপথে ঘোরার বা আবর্তনের কথা। যা বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবীকে আন্দোলিত না করার জন্য পাহাড়কে কিলকের মত স্থাপন করেছেন বলায় লেখিকা কোরআনে ভুল রয়েছে বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। ..পৃথিবী পতনের কথা কোরআনে বলা হয়নি। লেখিকার চপলতা নেহাতই মূর্খতার পরিচয়। তার বালিকাসুলভ অজ্ঞতাজনিত উক্তি নিতান্তই হাস্যকর। সুতরাং স্বল্প জ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞান আলোচনা না করাই উত্তম।..হুরকে কোরআনের এক জায়গায় আজওয়াজে মুতাহহারাত বলা হয়েছে অর্থাৎ পবিত্র সঙ্গিনী। সুতরাং পবিত্রের সঙ্গ যারা অপবিত্র কোনও কল্পনা করে, তারা তাদের নিজের কলুষিত মনেরই প্রকাশ করে থাকে। যারা কার্লমার্ক্সকে দেবতার মত মানে তাদের পিছে ঘুরলে শুধু মাথাই ঘুরবে কোনও লাভ হবে না। মার্কসবাদ কাল্পনিক মতবাদ তাই আজ আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। এদের পত্রিকায় ইসলাম বিরোধী মিথ্যা প্রবন্ধ ছাপানো সম্ভব হলেও এতে ইসলামের পবিত্র অঙ্গে কোনও দাগ পড়বে না। মুসলমানরা ঠিকমত কোরআন হাদিস মেনে চলছে না বলে পৃথিবীতে পিছিয়ে আছে। কিন্তু ইসলাম তথা আল্লাহর সর্বশেষ কিতাবে কোনও ভূল নেই, এটা অমুসলিমরাও মানতে বাধ্য হচ্ছে। যারা মানে না তারা আর যাই হোক মুসলমান নয় এবং ইসলাম তথা কোরআনের বিরুদ্ধে লিখার আগে আরও একটু পড়াশোনা করার দরকার নতুবা শুধু হাসির পাত্র হতে হবে। এ ধরনের অবিশ্বাসী মুসলমানরা মুসলিম নাম রেখে এদেশের যাবতীয় সুবিধা ভোগ করছে এটাও একটা বিরাট প্রতারণা ও ধোঁকা।’ যেহেতু আমি লিখেছিলাম যে আমাদের সৌরজগতের সঙ্গে আল্লাহতায়ালার সৌরজগতের কোনও মিল নেই, গোলাম মোয়াযযম উত্তরে বলছেন, ‘বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলাদেশে এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপা হয় জেনে খুব দুঃখ হচ্ছে এবং বোঝা যাচ্ছে এ দেশের শিক্ষার মান বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার মান কত নিম্নস্তরের ও মধ্যযুগীয়।’
মিল্লাত পত্রিকায় ফারিশতা তাঁর রোজনামচা লিখেছেন, ‘আমাদের দেশের এক নারী কলামিস্টের ধারণা পুরুষের হাতে গড়া এই পুরুষ প্রধান সমাজের স্বার্থের প্রয়োজনেই ধর্ম সৃষ্টি করে সুচতুর পুরুষ আর সেখানে স্বয়ং বিধাতাও নাকি নারী বিদ্বেষী। ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, ত্রিপিটক, বেদ, উপনিষদ এমনকী পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে কিছু কিছু অসংলগ্ন শ্লোক ও আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি হাজির করে অতি সম্প্রতি অকাল কুষ্মাণ্ড একটি দৈনিকের কলামে তিনি একটি প্রবন্ধ ফেঁদে তাঁর এই উদ্ভট ও বিকৃত চিন্তার ফসল বিষবৃক্ষে পানি সিঞ্চন করে ধর্মের সকল বন্ধন থেকে নারীকে মুক্ত করার অপচেষ্টা করেছেন। অবশ্য এর আগে পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায় পর্যায়ের এই লেখিকা সর্বভুক কাকের মত বহুবার সমাজ দেহের পরিত্যক্ত ও পরিত্যজ্য ময়লা ঠুকরিয়ে বের করে সমস্ত পরিবেশকেই দুর্গন্ধযুক্ত করার অপপ্রয়াস করেছেন। ধর্মীয় নিয়ম কানুনের প্রতি তাঁর প্রবল বিদ্বেষ এবং পুরুষের প্রতি তাঁর সীমাহীন আক্রোশ আমি তখন থেকেই লক্ষ্য করে এসেছি। আমি শুনে এসেছি যে, তিনি নাকি একজন সুশিক্ষিতা নারী এবং পেশায় একজন ডাক্তার। তাছাড়া তিনি নাকি একজন কবিও বটে। ধর্মবিরোধী ও পুরুষ বিদ্বেষী এই মহিলা কবির সাম্প্রতিক লেখা একটি তথাকথিত কবিতার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আমার এক আত্মীয়া। তাঁর কবিতা নামধারী এই পংক্তিমালার একাংশে লিখেছেন যে হাত ধরলেই মরণ। মনে হয় সেই ছেলেবেলা নাকি মেলাবেলা থেকেই কারও হাত ধরার প্রবল আকাঙ্খা ছিল তাঁর। কিন্তু বেশ কয়েকবার বেশ কয়েকজনের হাত ধরে যে অভিজ্ঞতা তাঁর সঞ্চিত হয়েছে, তাতে আর নতুন করে কারও হাত ধরার শখ তাঁর ফুরিয়ে গেছে। কি জানি! কিন্তু বাপু, যতদিন ওই পোড়া দেহটি আছে ততদিন যে কারও না কারও হাত ধরতেই হবে। তাছাড়া কাদায় বা গর্তে পড়লে কারও হাত ধরেই তো উঠতে হয়। কলামিস্ট সাহেবার অবস্থা দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনি এখন সত্যিই নাক অবধি দুর্গন্ধযুক্ত কাদায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন। আর এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে তাঁকে কারও হাত ধরেই উপরে উঠতে হবে। হাত ধরাকে তিনি যতই মন্দ বলুন না কেন, সঠিক হাত ধরতে পারলে সে হাত তাঁকে কেবল কর্দমামুক্ত করবে না তাঁকে বাঁচিয়েও তুলবে। ….নারীমুক্তি আন্দোলনে আপনার লেখা আরও সমৃদ্ধি আনবে যদি সঠিক হাত সত্যিই ধরতে পারেন। আমার ধারণা এ সমাজে নারীর দুর্গতি দেখে আপনি প্রতিনিয়ত আহত হচ্ছেন। আপনার অবলোকন পদ্ধতি সঠিক এবং আপনি লেখেনও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে। আপনি একজন ভাল লেখিকা। আহা আরও কত ভালই না হত, আপনি যদি ধর্মীয় বিষয়েও কেবলই একপেশে চিন্তা না করতেন।..’
কলকাতার মুসলমান মৌলবাদীরাও বসে নেই। সাপ্তাহিক কলম, মীযানে লেখা চলছে আমাকে আক্রমণ করে। নারী স্বাধীনতার ব্যপারটি ওদের পছন্দ নয়। প্রকৃতির উদাহরণ দিয়ে একজন লিখেছেন, পুরুষ হল সূর্য আর নারী হল চাঁদ। ‘আল্লাহ নারীকে দিয়েছেন কমনীয়তা আর পুরুষকে দিয়েছেন কঠোরতা। এ দুয়ের পরিপূরণে সার্থক ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় সমাজ ও পরিবার। এ দুয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জন্ম নেয় দ্বন্দ্ব সংঘাত, অশান্তি, অকল্যাণ। তসলিমারা নারী পুরুষের পরিপূরণ চায় না। চায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফলে পদে পদে ঘটছে বিপর্যয়। মৌলবাদীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লেখনীতে বক্তব্য রাখা যায়। কিন্তু মৌলবাদীদের মত নির্মল চরিত্র ও নীতি নৈতিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায় না। মৌলবাদীরা ইসলামের দর্শনে অনুপ্রাণিত। যৌগবাদীরা প্রবৃত্তির তাড়নায় উন্মাদ।’ আমার নিন্দা করে ওসব পত্রিকায় যে লেখাই ছাপা হয়, বাংলাদেশের মৌলবাদীরা নিজেদের কাগজে সগৌরবে তার পূনর্মুদ্রণ করে।
ভারতবর্ষের বাইরে বসেও আমার লেখা অনেকে পড়ছেন। দেশের বাইরেও দেশের মত আমার লেখা নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলে। লণ্ডন থেকে লেখক গোলাম মুরশিদ তাঁর ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে চলে এলেন আমার সাক্ষাৎকার নিতে। শফিক আহমেদ এবং তাঁর স্ত্রীও লণ্ডন থাকেন, সাহিত্য সংস্কৃতির জ্ঞান প্রচুর, আমার সঙ্গে দেখা করলেন দেশে এসেই। বোস্টনের মেঘনা দেশে বেড়াতে এসে আমার খোঁজ করে আমার জন্য ঝুড়ি ভরে আনা ভালবাসা রেখে গেলেন। একদিকে ভালবাসা। আরেকদিকে ঘৃণা। মাঝখানে আমি। ভালবাসা ঘৃণা দুটোই আমাকে নাড়ায়। তবে ভালবাসা আমাকে কাবু করে ফেলে না। ঘৃণাও না। আমি যেন ধীরে ধীরে দুটোই অন্তস্থ করার জন্য অথবা দুটো থেকেই মুক্ত হবার জন্য নিজেকে নির্মাণ করছি। আমার লেখা নিয়ে যাদের অতি আবেগ সে ভালবাসা বা ঘৃণা যেটিই হোক, আমাকে মাঝে মাঝে বড় অপ্রতিভ করে তোলে। একবার টাঙ্গাইল থেকে এক মেয়ে এল আমার বাড়িতে। মেয়েটি কলেজ পাশ করেছে, এখন চাইছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে কিন্তু বাড়ি থেকে কিছুতেই তাকে পড়তে দেবে না। মেয়ে চলে এসেছে পালিয়ে আমার কাছে। আমিই যেন এখন আশ্রয় তার। যেন আমিই জানি এখন তার কী করতে হবে। আমার লেখা পছন্দ করে বলে বাড়িতে মেয়েটি চড় থাপ্পড় খেয়েছে। গালিগালাজ শুনেছে। তারপরও সে দমে যায়নি। জোর গলায় বলেছে যে তার জীবনে আমার চেয়ে বড় অন্য কেউ নেই। না বাবা মা, না ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন। ভগবান বা আল্লাহ বলে কোথাও কিছু থেকেও থাকে, সেও এত বড় নয়। কেবল অল্প বয়সী মেয়েই নয়, মধ্যবয়সীদেরও ভিড় হয়। পনেরো থেকে পঁচাত্তর সব বয়সীই সব পেশার সব শ্রেণীর মেয়ে মহিলা আমার দরজায় কড়া নাড়ে। সকলেই নিজের জীবনের সব কথা অকপটে বলে আমাকে। আমি কষ্টের বিভিন্ন রূপ দেখি, বিভিন্ন রঙ দেখি। অনেকে আমার কাছে শক্তি চায়, সাহস চায়। আমি কি যোগাতে পারি কোনও শক্তি বা সাহস! আমার মনে হয় না। অনেকে হতাশা নিয়ে ফিরে যায়। কেউ কেউ আঠার মত লেগে থাকে, জানি না কী পায় আমার মধ্যে। নাহিদ নামের এক মেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্রী, দেখা করতে এল। দেখা করতে এলে কথাবার্তা বলে বিদেয় হওয়ার কথা। কিন্তু বিদেয় হতে চায় না। বিদেয় হলেও কদিন পর আবার দরজায় চেহারাটি উঁকি দেয়। ঝুনু নামের এক মেয়ে, রাজনীতি করে, দেখা করতে এল। বসতে দেওয়া হল। চা বিস্কুট দেওয়া হল। এরপরও বসে থাকে। একটু ছুঁয়ে দেখতে চায় আমাকে। মিতুল এল, নিপা এল, দুই বুদ্ধিদীপ্ত রূপসী কিশোরী, ভিখারুন্নেসা ইস্কুলের ছাত্রী। এদের আসা ক্রমশ নিয়মিত হয়ে উঠল আমার শান্তিবাগের বাড়িতে। মামুন আর আনু, অল্প বয়সী দম্পতি, এদের আসাও নিয়মিত, আনু একটি দোকানে জিনিসপত্র বিক্রি করার কাজ নিয়েছে, মামুনের চাকরি নেই। অভাবের সংসার ওদের। একদিন ভোরের কাগজের সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখে মামুনকে পাঠিয়ে দিই সম্ভব হলে একটি চাকরি যেন ছেলেটিকে দেওয়া হয়। মামুনের লেখা কিছু চিঠি পড়েই বুঝেছি ছেলেটির লেখার হাত খুব ভাল। ভোরের কাগজে মামুনের চাকরি হয়। আমার দিন যেতে থাকে হাসপাতালের কাজে, সংসারে, লেখায়, আড্ডায় আর ভক্তকূল সামলানোয়। গুরুর আচরণ যেহেতু আমার স্বভাবে চরিত্রে নেই, ভক্তকূল অচিরে বন্ধুর মত হয়ে ওঠে, বাড়ির লোকের মত। অবাধ বিচরণ তাদের আমার বাড়িতে।
আজকাল মোল্লা মুন্সি দেখলে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যাই। এদের আস্ফালন দেখে মনে হয় আমাকে বুঝি কাঁচা খেয়ে ফেলবে। কিন্তু তারপরও হঠাৎ হঠাৎ অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড ঘটে। একদিন দাড়িঅলা লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরা এক লোক সোজা ঢুকে গেল আমার বাড়িতে। বাড়িতে আসা যাওয়ার সময় কেউ হয়ত বাইরের দরজাখানা খুলে রেখেছিল। বাড়ির সবাই আমার শোবার ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছে। হঠাৎ অচেনা একটি লোককে শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে আমি আর্তনাদ করতেও ভুলে যাই ভয়ে। কী চায় এই লোক! এখানে কেন! আমার হতভম্ব মুখের দিকে চেয়ে লোকটি বলল, ‘ভয় পাবেন না, আমি কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়া আসি নাই। আপনাকে এক পলক দেখতে এসেছিলাম। বহুদিনের ইচ্ছ! ছিল আপনাকে একবার দেখব। আজ আমার জীবন সার্থক হল।’
অনাকাঙ্খিত অতিথিকে খুব দ্রুত বাড়ির বাইরে বের করে দেওয়া হল। লোকটি কি সত্যিই জীবন সার্থক করতে ওভাবে বেড়ালের মত ঢুকেছিল বাড়িতে!
১৭. যেমন খুশি তেমন সাজো
সত্যিই কি কোনও প্রেম করেছি আমি নাকি প্রেমের ধারণাট্ি বয়ে বেরিয়েছি কেবল? এই একটি অদ্ভুত প্রশ্ন আমি করতে শুরু করি নিজেকে। রুদ্রর সঙ্গে আমার যে সম্পর্কটি ছিল, তাকে কী কী কারণে প্রেম বলা যায় এবং কী কী কারণে বলা যায় না, তার একটি হিসেব কষে দেখি রুদ্রর জন্য আমার আকর্ষণ তীব্র ছিল বটে, রুদ্রর অনাচার আমাকে রুদ্র থেকে দীর্ঘদিন ফেরায়নি বটে, এর পেছনের কারণ প্রেম নয়, অন্যকিছু। অন্যকিছুতে আছে নিঃসঙ্গতা, আছে প্রেম করার আগ্রহ এবং প্রেমের ধারণা। প্রেম করলে সামাজিক যে আচরণটি মানুষ করে সেটি আমি জেনেছিলাম বলে আচরণটি আমি করে গেছি। আচরণটি শেখা। আচরণটি নিজস্ব নয়। রুদ্রর কিছু কবিতা আমি সাপ্তাহিক পত্রিকায় পড়েছিলাম, এইমাত্রই। এরপর একদিন রুদ্রর চিঠি পাই আমি, যখন সে আমার সম্পাদিক কবিতা পত্রিকা সেঁজুতির জন্য কবিতা পাঠায়। উত্তরে আমিও চিঠি লিখি। এভাবেই চিঠির যোগাযোগ। যাকে কোনওদিন দেখিনি, যার সম্পর্কে জানি না কিছু তার প্রেমে পড়ে গেলাম! দেখতে রুদ্র কোনও অর্থেই সুপুরুষ ছিল না, তাকে প্রথম দেখে আমার বিবমিষা ছাড়া আর কিছুর উদ্রেক হয়নি। রুদ্রর কবিতা আমার ভাল লাগত, এরকম তো কত কারও কবিতাই আমার ভাল লাগে। প্রেমে আসলে আমি পড়েছিলাম প্রেম ব্যপারটির।
কৈশোরে আমি আর চন্দনা প্রেমে পড়েছিলাম সিনেমার নায়ক জাফর ইকবালের। জাফর ইকবালের রূপ আমাদের আকর্ষণ করেছিল। আকর্ষণের জন্য কিছু না কিছু থাকতে হয়। রূপ নয় গুণ। কিন্তু সেটিও সত্যিকার প্রেম নয়। কিশোর বয়সে এমন হয়ই। জাফর ইকবালের সঙ্গে চিঠিতে বন্ধুত্ব হয়েছিল আমাদের। জাফর এমনকী চন্দনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিল। জাফরের সঙ্গে কোনও একদিন সত্যিকার দেখা হবে, এরকম একটি স্বপ্ন ছিল আমার। স্বপ্নটি আমি লালন করেছি দীর্ঘকাল। ঢাকায় জাফর ইকবালের পাঁচ নয়াপল্টনের বাড়ির সামনে দিয়েই ছোটদার বাড়িতে গিয়েছি, কোনওদিন ঢুকিনি তার বাড়িতে। হবে একদিন দেখা, কোথাও একদিন দেখা হবে। নাহ, দেখা হয়নি। দেখা হবেও না কোনওদিন। দেশের সবচেয়ে সুদর্শন নায়কটি অল্প বয়সে হঠাৎ একদিন ভোরবেলা মরে গেল। কোনও অসুখ নেই, বিসুখ নেই। সুস্থ সবল একটি মানুষ মরে গেল! কী অবিশ্বাস্য গা অবশ করা খবর! সোনিয়া নামের এক মেয়েকে জাফর বিয়ে করেছিল, সোনিয়ার সঙ্গে তার মনের মিল হয়নি, সোনিয়া চলে গিয়েছিল জাফরকে ছেড়ে, সে কারণেই কি না জানি না বিরহে একাকীত্বে অতিরিক্ত মদ্যপানে নিজের মৃত্যু ঘটিয়েছে সে।
যখন থেকে হিন্দি ছবি দেখতে শুরু করি, অমিতাভ বচ্চনের জন্য কি রকম পাগল পাগল লাগত। আবার অমিতাভ যখন রেখার সঙ্গে প্রেম করত, তা দেখতেও ভাল লাগত। রেখার সঙ্গে মানাত খুব অমিতাভকে। নিজে মনে মনে রেখা হয়ে অমিতাভের প্রেম গ্রহণ করতাম। কিন্তু রেখা তো আমি নই। আমি আমিই। আমাকে ভালবাসার জন্য কোনও সুদর্শন যুবক কোথাও অপেক্ষা করে নেই। আমিই কেবল বসে বসে সুদর্শন সুপুরুষের অপেক্ষা করি। কৈশোর কাটলে আফজাল হোসেনের সঙ্গে আমার খুব প্রেম করতে ইচ্ছে হত। সত্যি বলতে কী, এই ইচ্ছেটি আমার কোনওদিনই চলে যায়নি। আফজাল অতি সুদর্শন ছেলে। নাটকের ছেলে। টেলিভিশন আর মঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেতা আফজাল। নিজে নাটক লেখে। চমৎকার সব প্রেমের গল্প। নতুন উপন্যাসও লিখছে। প্রকাশক বিদ্যাপ্রকাশ। খোকাই তাগাদা দিয়ে দিয়ে আফজালকে লেখাচ্ছেন। আফজালকে আমি প্রথম দেখি দশ আগে ফেব্রুয়ারির বইমেলায়। এত লম্বা যে কোনও কেনা প্যাণ্ট তার আঁটে না, গোঁড়ালির ওপর প্যান্ট উঠে আছে, সেটি পরেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেলায়। রুদ্রর সঙ্গে পরিচয় ছিল আফজালের। আফজালকে ডেকে রুদ্র কথা বলল। এরপর আরও দুএকদিন এখানে সেখানে টুকরো টুকরো দেখা হয়েছে। নাটকের মেয়ে সুবর্ণার সঙ্গে আফজালের প্রেম ছিল। কিন্তু সে প্রেম একসময় ভেঙে যায়। আফজাল একা হয়ে গেল। মাত্রা নামে নয়াপল্টনে, ঠিক ছোটদার বাড়ির পেছনে একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা খুলে বসল। ছোটদার বাড়িতে যেতে আসতে দেখি মাত্রার আপিস। রুদ্রর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকাকালীন আফজাল-মোহটি সংস্কার-চাপা ছিল। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর কতবার যে মাত্রা ছাড়া আবেগ উথলে উঠে আমাকে মাত্রায় ঢোকাতে চেয়েছে, ঢুকিয়ে বলাতে চেয়েছে ভালবাসার কথা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সৌন্দর্যের পাশে মনে মনে আফজালকে দাঁড় করিয়ে দেখেছি চমৎকার মানাচ্ছে। তারপরও মাত্রায় আমার ঢোকা হয়নি, বলা হয়নি কিছু। আবেগের লাগাম টেনে ধরেছি প্রতিবারই। অনেক বছর আগে, ময়মনসিংহের দুই কবি শফিকুল ইসলাম সেলিম আর আতাউল করিম সফিক আফজাল হোসেন আর ইমদাদুল হক মিলনকে ময়মনসিংহে নিয়ে ছিল অনুষ্ঠান করতে। মহাকালি ইশকুলে অনুষ্ঠান। সেলিম আর সফিকের অনুরোধে সেই অনুষ্ঠানে আমার গল্প পড়তে যেতে হল। তখন আমি কয়েকটি গল্প লিখেছি সংবাদ পত্রিকার মেয়েদের পাতায়। মাধবীর জীবন কথা গল্পটি সাধু ভাষায় লেখা। এটি আমার গল্পগুলোর মধ্যে আমার বিচারে সবচেয়ে ভাল। অনেকের গল্প পড়ার পর একেবারে শেষে অতিথিদের গল্প পড়ার আগে ছিল আমার গল্প পড়া। কিন্তু পড়তে উঠে বিচ্ছিরি কাণ্ড শুরু হল। দর্শকরা হৈ হৈ করতে শুরু করল। কেউ আমার গল্প পড়া শুনতে চায় না। হৈ হৈ এর মধ্যে গল্পের সামান্য অংশ পড়ে আমাকে মঞ্চ থেকে নেমে পড়তে হয়েছে। বাধ্য হয়েছি নেমে পড়তে। আমার জানা হয়নি হৈ হৈ কি আমাকে অপছন্দ করার কারণে নাকি অতিথিদের গল্প শোনার জন্য অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিল শ্রোতারা, সে কারণে। যে কারণেই হোক আমার আর সে রাতে আফজাল বা মিলন কারও সঙ্গে কথা বলার মুখ ছিল না! ওই হৈ হৈ ঘটনার কথা মনে পড়লেই মাত্রায় নেমে আফজালকে ভালবাসার কথাটি বলার যে কল্পনাটি হঠাৎ হঠাৎ করি, সেটিকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিই। আফজালের মাত্রায় আমি গিয়েছি ঠিকই একদিন, তবে আফজালের জন্য নয়, মিলনের জন্য। তখন আমি আর মিলন ভারতে বেড়াতে যাবো। মিলনের বিকেল কাটত মাত্রায় আড্ডা দিয়ে। মিলন বলেছিল তার সঙ্গে মাত্রায় দেখা করতে। মাত্রায় মিলন নেই এ কথাটি আফজাল আমাকে জানিয়ে দিলেই পারত। কিন্তু আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে দরজা থেকে নিয়ে গেল তার ঘরে। বসালো। চা খাওয়ালো। অনেকক্ষণ বিজ্ঞাপন নিয়ে নাটক উপন্যাস নিয়ে কথা বলল। একটি মোটা ইংরেজি উপন্যাস আমাকে উপহার দিল। যাবার সময় দরজা পর্যন্ত এল বিদায় দিতে। আবার যেতে বলল। এমন আদর আমার প্রত্যাশিত ছিল না। সেদিন সারাদিন তিরতির করা একটি সুখ আমার হৃদয়ের শীতল য়চ্ছ জলে সাঁতার কেটে বেড়ালো। আফজালের সঙ্গে আমার শেষ দেখাটি এই সেদিন, খোকার বাড়িতে। খোকা আমাকে নেমন্তন্ন করলেন তাঁর বাড়িতে। সন্ধেবেলায় হঠাৎ ফোন তাঁর, এক্ষুনি চলে আসেন। কেন? রাতে খাবেন, আমার বউ রান্না করেছে। তখনই যে শাড়ি সামনে ছিল সেটি পরে সোজা চলে যাই খোকার বাড়িতে রিক্সা নিয়ে। খানিকটা আলু থালু, খানিকটা ঘরোয়া বেশে খোকার বাড়িতে ঢুকি। ভেবেছিলাম আমাকেই কেবল খেতে বলেছেন খোকা। কিন্তু ঘরে ঢুকে চমকে উঠি। দেখি আফজাল বসে আছে, সঙ্গে তার স্ত্রী। নতুন বিয়ে করেছে, বউকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বিয়ে করেছে বলে, বউ আছে বলে সঙ্গে আফজাল-মোহ আমার দূর হয়নি মোটেও। কিন্তু সমস্ত আবেগ আমি কিছু একটার তলে চাপা দিয়ে রাখি। প্রকাশক তাঁর দুই লেখককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। লেখক আফজালের সঙ্গে লেখক তসলিমার যে রকম সৌজন্য কথাবার্তা হওয়া মানায় সেরকমই কথা হয়েছে। তখন আমি আর সেই হৈ হৈ করা দর্শক শ্রোতার সামনে গল্প পাঠ না করতে পেরে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বাধ্য হওয়া তসলিমা নই, দেশের জনপ্রিয় লেখক, আনন্দ পুরস্কার পাওয়া তসলিমা। তবে কোনও অহংকার আমার চিবুক উঁচু করায়নি। যে মানুষের জন্য গোপনে গোপনে তৃষ্ণা থাকে, তার সামনে এলে সব অহংকার কাঁচের বাসনের মত ভেঙে পড়ে।
স্বপ্নের পুরুষ স্বপ্নেই থেকে যাওয়াটা হয়ত ভাল। নিত্যদিনের সংসারযাপনে স্বপ্নকে এনে ধুলো না লাগানোই হয়ত ভাল। স্বপ্ন চিরকাল নাগালের বাইরে থাক, পরিচ্ছত থাক, ঝকঝকে সুন্দর থাক। ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাক স্বপ্ন। জীবন ভর স্বপ্নের ঘুড়ি ওড়াবো আকাশে, কোনওদিন ভোঁ কাট্টা না হোক সেই ঘুড়ি। আনন্দ থাক স্বপ্ন নিয়ে। এই ভেবে ভেবে স্বপ্নকে দূরে রেখেছি নিজের দুঃখ শোক থেকে, নিজের কালি কালিমা থেকে। নিজেকে বরং ধুলো কাদায় মাখিয়েছি। শরীরের প্রয়োজনে শরীর বিনিময় হয়েছে কিছু পুরুষের সঙ্গে। প্রথম শরীরী সুখ আবিস্কারের উত্তেজনা ছিল রুদ্রর সঙ্গে। রুদ্র যখন জীবনে নেই, তখন এক এক করে মিলন, নাইম, মিনারের সঙ্গে হল শরীরের ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা। এ খেলায় আমার সুখ হলেও তাদের সুখই ছিল প্রধান। কলকাতায় জালালের সঙ্গেও তিনটে রাত কেটেছে বিচিত্র সম্ভোগে। এক সন্ধেবেলায় এসে জীবনের গল্প বলেছিল সে। সারারাত তার গল্প শুনেছি, কী করে তার প্রেম হয়েছিল, বিয়ে হয়েছিল, কী করে সেই বিয়ে ভেঙেছে, কি করে একাকীত্ব তাকে নাশ করে দিচ্ছে। মদ্যপান করতে করতে কথা বলছিল সে, ভোর হবার আগে আগে মদ্য পান শেষ হলে হঠাৎ আমাকেই আমূল পান করতে শুরু করে। আমি না বলি না। না বলি না এই কারণে যে, আমি না বলতে পারি না তা নয়, না বলার কোনও প্রয়োজন মনে করি না, তাই না বলি না। জালাল আমার প্রেমে পড়েনি, সে তখন প্রেম করছিল চিত্রা লাহিড়ী নামের এক উঠতি কবির সঙ্গে। শরীর তো হল, কিন্তু শরীরই তো শেষ কথা নয়। বাঁশির সঙ্গে প্রেম না হলে বাঁশি দীর্ঘদিন বাজে না। আমার আনন্দ পুরস্কার পাওয়ার খবরে জালাল খুশি হয়েছিল, কিন্তু খুশিটি কি তেমন খুশি ছিল! একটি চিকন ঈর্ষা দেখেছি তার চোখের তারায়। পুরস্কার অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে বলেছিল, আমি নাকি যৌন শব্দটি খুব বেশি ব্যবহার করেছি। অবশ্য বলেছে এটি তার নিজের মন্তব্য নয়, অনুষ্ঠানে তার পাশের চেয়ারে বসা একটি লোকের মন্তব্য। কিন্তু কেন জালাল এটি শোনাতে গেল আমাকে! তার নিজেরও হয়ত তাই মনে হয়েছে। জালাল যৌনতাকে গোপনে রাতের জন্য রেখে দিতে চায়, যৌনতার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও মেয়ের একলা ঘরে গিয়ে নিজের করুণ গল্প শুনিয়ে মেয়েকে কাতর করে মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে নিজের যৌনক্ষুধা মেটাতে চায়, কিন্তু দিনের আলো ফুটলে জনসমক্ষে যৌনতার কোনও প্রসঙ্গ সে প্রসঙ্গ শ্লীল হলেও জিভে আনা তার কাছে অশ্লীলতা। মুসলমান ঘটিদের মুসলমানের শহর ঢাকায় বেড়ানোর খুব শখ। জালাল ঢাকায় বেড়াতে এসে আমার বাড়িতে উঠেছে। অবশ্য আমি কোনও সঙ্গ দিতে পারিনি, নিজেই সে ঘুরে বেড়িয়েছে একা, চেনা পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করেছে। জালালের কোনও গল্প আমাকে আর কাতর করেনি। আসলে আমার সময়ই ছিল না তার গল্প শোনার। বাড়িতে সে স্নান করছে, খাচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে, ফিরে আসছে। আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি হয়নি। ত্রুটি হয়ত ছিল না, কিন্তু শীতলতা ছিল। জালাল যদি ভেবে থাকে যে আমার শরীরটি সে হাত বাড়ালেই পাবে, তবে তার ভাবনার ঘাড়ে একটি হাতুড়ির আঘাত পড়েছে এই যা। রাতে আমি আমার ঘরের দরজা ভাল করে সেঁটে ঘুমিয়েছি। জালাল মিলনের ঘরে গিয়ে কখন ঘুমিয়েছে, কখন উঠেছে তার কোনও খবর রাখা আমার হয়ে ওঠেনি। আমার তো ভোরবেলা হাসপাতালে চলে যেতে হয়। আমার তো গোটা দিন বা রাতের অবসর নেই যে সময় দেব! কলকাতা আর ঢাকা এক নয়। কলকাতায় আমি ছুটি কাটাই। ঢাকায় আমার আকণ্ঠ ব্যস্ততা। শরীরে পুরুষের স্পর্শ না থাকলেই শরীর যে কোনও পুরুষের জন্য জেগে ওঠে না। এ শরীরের অভ্যেস আছে পুরুষস্পর্শহীন দীর্ঘবছর কাটিয়ে দেওয়ার। তাছাড়া খানিকটা হলেও মন চাই। অতি রাতে অতি আবেগে কিছু অতিউর্বর শুক্রাণুর আক্রমণে ঋতুস্রাব বন্ধ করে বসে থাকব, আর নাইম এসে নিজের কীর্তি ভেবে গর্ভপাতে সাহায্য করবে, এতে নাইমের ওপর শোধ নেওয়া হয়ত হয়, আমার শরীরে বা মনে কোনও সুখ হয় না। জালাল বলে আমি নাকি খুব পাল্টো গেছি। পাল্টো হয়ত কিছুটা গেছিই, পাল্টাবো না কেন, মন তখন আমার কায়সারে।
আমার যদিও বিশ্বাস ছিল, পুরুষের সঙ্গে প্রেম এ জীবনে আমি আর করছি না অথবা কোনও পুরুষের সঙ্গে নিজের এই জীবনটি আমি আর জড়াচ্ছি না, কিন্তু খানিকটা জড়িয়ে পড়ি আমি, অনেকটা ইচ্ছে করেই পড়ি। ভেবেছিলাম নিজের সংসার নিয়ে, ডাক্তারি নিয়ে,সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে চমৎকার বাকি জীবন কাটিয়ে দেব, পুরুষের কোনও প্রয়োজন আমার জীবনে নেই। কিন্তু একদিন ঠিকই আশ্চর্য সুন্দর এক যুবককে দেখে চোখ ফেরাতে পারি না। বার বার চোখ যায় যুবকের দৈর্ঘে প্রস্থে, ডাগর দুটো চোখে, খাড়া নাকে, যুবকের গোলাপি ঠোঁটে, মিষ্টি হাসিতে। যে তৃষ্ণাতুর চোখে পুরুষেরা দেখে কোনও রূপবতী রমণীকে, সে চোখে আমি কায়সারের রূপ দেখি। সুদর্শন যুবকের জন্য আকাঙ্খা আমার সারা জীবনের। জীবনে সাধ মেটেনি। সাধ না মেটা হৃদয়টি কায়সারকে কামনা করে। অবশ্য মনে মনে। কিন্তু মনের কথাটি খুব বেশিদিন মনের মধ্যে বসে থাকেনি। শেরাটনের স্ক্রু ড্রাইভার এক রাতে হাট করে খুলে দিল বন্ধ অর্গল। কায়সার কোনও ডাক্তার নয়, লেখক নয়। কায়সার আমার কোনও বই পড়েনি। কলকাতার আজকাল পত্রিকার সাংবাদিক বাহারউদ্দিন আমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন তাঁর জয়দেবপুরের বন্ধু কায়সারকে নিয়ে। তখনই কায়সারকে আমি প্রথম দেখি। বাহারউদ্দিন কলকাতা ফিরে যান, কিন্তু কায়সার ফিরে ফিরে আসে আমার বাড়িতে। কায়সারের জগত আর আমার জগতে কোনও মিল নেই। এক জগতের মানুষের সঙ্গে তো অনেক হয়েছে, এবার অন্য জগতে ঢুকে দেখি না কেন, কেমন সে জগতের চেহারা! টেলিফোনের জন্য আবেদন করে রেখেছি বছর আগে, এখনও টেলিফোন পাওয়ার খবর নেই। কায়সার আগ বাড়িয়ে বলে, সে চেষ্টা করবে টেলিফোন পেতে, তবে আমাকে যেতে হবে টেলিফোন মন্ত্রীর বাড়ি। আমাকে সে টেলিফোন মন্ত্রীর বাড়িতে নিয়ে যায় একদিন। বাড়ি যাওয়া মানে চা বিস্কুট খাওয়া আর মন্ত্রী যা বলবে, মন দিয়ে শোনা আর হেসে বিদেয় নেওয়া। কায়সারের অনুরোধে মন্ত্রী আমার টেলিফোনের আবেদনে নজর দেন। সে কারণেই আমার টেলিফোন পাওয়া হল। তা না হলে টেলিফোনের দেখা কখনও মিলত কী না সন্দেহ। ময়মনসিংহের বাড়িতে আমি নিজে টেলিফোন নিয়েছিলাম, আমাকে কোনও মন্ত্রীর বাড়ি দৌড়োতে হয়নি, আবেদন করেছি, মিলেছে। কিন্তু ঢাকা যেহেতু ময়মনসিংহ নয়, তাই শুধূ আবেদনে চিড়ে ভেজে না। আজকাল দুর্নীতি এমনই বেড়েছে দেশটিতে যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঘুষ না দিয়ে কোনও আবেদনের কাগজ এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে সরানো যায় না। ওপরতলায় খাতির থাকলেই কাগজের পা গজায়। কায়সারের কল্যাণে বাড়িতে টেলিফোন আসায় তার কদর বেড়ে যায় আমার বাড়িতে। এরশাদ আমলে কায়সার ছিল গাজিপুর উপজেলার চেয়ারম্যান। এ নিয়ে তার অহংকারের শেষ নেই। কায়সারের জগত সম্পর্কে যখন আরও জানা হয় আমার, দেখি সেই জগতটি ক্ষমতার রাজনীতির আর দুর্বোধ্য ব্যবসা বাণিজ্যের। কায়সার কোনও বড় রুই কাতলা নয়, নিতান্তই পুঁটি মাছ এই ঘোলা পুকুরে। রুই কাতলা হওয়ার শখ তার খুব। কায়সার যখন বীরদর্পে তার সম্পর্কে যেন উচ্চ ধারণা লালন করি, বলতে থাকে যে তার সঙ্গে এই মন্ত্রীর চেনা আছে, ওই মন্ত্রী তার বন্ধু, এই নেতা তার আত্মীয়, ওই নেতা তাকে মান্য করে, শুনতে বড় জঘন্য লাগে। আমি বুঝি যে কায়সারের জীবন আর আমার জীবন সম্পূর্ণই আলাদা। তার ওপর কায়সার বিবাহিত, ঘরে দুটো মেয়ে আছে। একজনের নাম অনন্যা আরেকজনের নাম সুখ। সুখ নামটি, কী অদ্ভুত, আমি ভেবেছিলাম নিজের যদি কখনও মেয়ে হয়, রাখব। কায়সারের বউ হেনু, বেটে, ধবধবে ফর্সা গোলগাল মেয়েমানুষ। হেনুর সঙ্গে একবারই মাত্র আমার দেখা হয়েছে। তাও নির্মলেন্দু গুণের কারণে। গাড়িতে হেনুকে রেখে কায়সার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। গুণ তখন আমার বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে গাড়িটি দেখেন। ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে বসা গাড়িতে, কায়সারের বউ নাকি!’ কায়সারের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। এরপর আমিই কায়সার আর গুণকে নিয়ে নিচে যাই বউটিকে দেখতে। হেনুর কথা কায়সার পারতপক্ষে আমার কাছে বলে না, আমি জানতে চাইলে দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টো ফেলে। হেনুকে নিয়ে এমন কী নিজের দুটো মেয়ে নিয়েও তার অস্বস্তির শেষ নেই। যদি প্রমাণ করতে পারত যে বাড়িতে তার কেবল মা আছে, ভাই আছে, কোনও বউ বাচ্চা নেই, তাহলে যেন সে আরাম পেত। কিন্তু কায়সারের বউ বাচ্চা নিয়ে আমার কোনও অস্বস্তি হয় না যখন সে মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকায় বা আমার একটি হাত সে ছুঁতে চায় নিঃশব্দে। আমি আমার হাতটিকে দূরে সরিয়ে রাখি না। যখন ঠোঁট বাড়ায় ঠোঁটের দিকে, খুব সহজেই আমার ঠোঁট কায়সারের ঠোঁটের নাগালে চলে আসে। এটি যত না কায়সারের প্রয়োজনে, তার চেয়ে বেশি আমার নিজের প্রয়োজনে। কায়সার চুপসে থাকে প্রথম দিন, আমার উথলিত উষ্ণ শরীরটির ওপর তার আশঙ্কার আঙুল কাঁপে। ধীরে ধীরে তার সংকোচের বরফ গলে যায় আমার উষ্ণতায়। আমার ছিল শরীরের প্রয়োজন, তার ছিল মনের। কায়সারের শরীর আমাকে দেয় আনন্দ, আমার দ্যূতি তাকে দেয় তৃপ্তি। কায়সারের সঙ্গে আমার কোনও বাঁধন গড়ে ওঠে না। মুক্ত একটি সম্পর্ক আমাদের। যে সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কারও নাক গলানো নেই। সম্পর্কটি নিরেট প্রয়োজনের জন্য, অথবা ঠিক তার জন্যও নয়। সম্পর্কটি কিছুর জন্যই নয়, যদি কিছুর জন্য হয়ও, ঠিক কিসের জন্য তা নিয়ে কেউই আমরা প্রশ্ন করি না, সম্পর্কটি টিকে থাকে, সম্পর্কটিতে কোনও ক্ষতি নেই বলে সম্পর্কটি টিকে থাকে। কায়সার এমন যে তাকে না হলেও চলে, আবার তাকে না হলেও চলে না। পর পর চারদিন এল কায়সার, এরপর পাঁচ দিনের না এলে মনে হয় কী যেন কি হয়নি আজ। এ বাড়িতে সে অনেকটা অভ্যেসের মত। দু সপ্তাহ আসেনি, দুসপ্তাহ পর হঠাৎ তার উপস্থিতি খানিকটা চমক আনে।
‘কী কায়সার ভাই। আপনে ত লাপাত্তা হইয়া গেছেন। এই বাড়ির রাস্তা ভুইলা গেছেন নাকি! খিরাজ টিরাজ আজকাল কেমন জুটতাছে কন!’
‘দূর মিলন, বাজে কথা বলবা না ত!’
কায়সার গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে।
কায়সারের চেয়ারম্যানি এখন নেই আর। জয়দেবপুর থেকে প্রতিদিন ঢাকা এসে মতিঝিলের বিভিন্ন আপিসে ঢুঁ মারে। আমি অনুমান করতে পারি না তার জীবিকার উৎস। বলে তার ব্যবসা আছে, পার্টনার আছে, পার্টনারদের সঙ্গে ব্যবসার কথাবার্তা বলতে সে ঢাকা আসে। কায়সারের জীবিকা নিয়ে যখন প্রশ্ন জাগে, মিলন বলে, ‘আরে বুবু, বুঝেন না কেন, কায়সার ভাই খিরাজ খায়।’
‘খিরাজ!’
‘হ খিরাজ খায়।’
খিরাজ শব্দটি আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। খিরাজ মানে কি জিজ্ঞেস করলে মিলন বলে ‘এই আর কি! তোমার ইন্ডাস্ট্রি আমার এলাকায় আছে, তা আমারে কিছু টাকা পয়সা দেও, আমি তোমার ইন্ডাস্ট্রি সামলানোর চেষ্টা করব, কোনও বদলোক তোমার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি করতে পারবে না। চেয়ারম্যান থাকাকালীন কাউরে বোধহয় ব্যবসায় হেল্প করছিল ক্ষমতা খাডাইয়া, তাদের কাছ থেকে এহন আদায় করে।’
কায়সার এলে জিজ্ঞেস করি, ‘কিরে তুই নাকি খিরাজ খাস?’ খুব অল্পদিনেই সম্বোধন তুইএ চলে এসেছে। আপনি থেকে তুমির সিঁড়িতে পা না দিয়েই লম্ফ দিয়ে তুই এ।
কায়সার মুচকি হাসে। খিরাজ শব্দটি তাকেও হাসায়। এই যে আমি ভাবছি তাকে নিয়ে, তার খিরাজ নিয়ে হলেও তাকে নিয়েই তো ভাবছি, এটুকুই তাকে আনন্দ দেয়। কায়সারের মুচকি হাসিটি সহজে সরতে চায় না।
আমাদের সম্পর্কটি কোনও অর্থেই প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক নয়, যদিও কায়সার মনে প্রাণে তাই কামনা করে, কিন্তু কায়সারকে প্রেমিক ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। কায়সার বন্ধুর মত। ঘরের লোকের মত। কুলসুম নেই বাড়িতে, ঘর মোছা হচ্ছে না কদিন, কায়সারই জামা জুতো খুলে নেমে পড়ে ঘর মুছতে। প্রতিটি আদেশ অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। কায়সার বোঝে যে তার প্রেমে আমি পড়িনি। আমার প্রেমিক হওয়ার জন্য সে মরিয়া হয়ে ওঠে। আমি তাকে সুন্দর বললে সে এমনি আহ্লাদে আটখানা হয় যে সারা মুখ ঝিলমিল করে, মাত্র ছমাস বা বছর খানিক আগে, গর্বিত গ্রীবা নেড়ে বলে, যে, সে আরও সুন্দর ছিল। কায়সারকে দুবছর বয়সী শিশুর মত মনে হয় আমার মাঝে মাঝে। কেবল যে শিশুসুলভ আচরণই সে করে তা নয়। হিংসুটে প্রেমিকের মতও তার আচরণ। আমার বাড়িতে যে লোকই আসে, তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। সন্দেহ, কারও সঙ্গে বুঝি গোপনে গোপনে আমার প্রেম হচ্ছে। কায়সারের সন্দেহ দেখে হাসি পায় আবার রাগও ধরে। তার হীনমন্যতার আমি পরোয়া করি না। তাকে পাত্তা দিলেই সে খুশিতে নাচে। পাত্তা না পেলে পাগল হয়ে ওঠে, এই বুঝি তাকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি! না, কায়সারকে ছুঁড়ে ফেলার আদপেই কোনও ইচ্ছে আমার নেই। তবে আমাকে সে কোনও কারণে বিরক্ত করুক তা আমি চাই না। বিরক্ত আমি নিজেকে হতে দিই না। যখনই সে তার কুটকচালের মুখ খোলে, সোজা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিই। আমার জীবনে কোনও হর্তাকর্তা রাখতে আমি রাজি নই। ‘খসরু কে? কেন আসে? কী চায়? আলমগীর লোকটিকে কেন আমি ঢুকতে দিচ্ছি বাড়িতে? রশীদের সঙ্গে কি সম্পর্ক!’ এসব প্রশ্ন করতে গিয়ে সে দেখেছে যে আমি কিছুতেই তার ঘোঁট পাকানো ঘোঁৎ ঘোঁৎ সহ্য করি না। ঔদ্ধত্য আর যেখানেই সে দেখাক, আমার কাছে নয। আমার বাড়িতে কে আসবে না আসবে, আমার জীবন কি করে কি ভাবে চলবে সে আমি বুঝব।
কায়সার নিজের ধনদৌলতের গল্প প্রায়ই করে। তার অঢেল সম্পদ। অঢেল টাকা পয়সা। ঢাকায় বাড়ি বানাচ্ছে সে। নতুন একটি গাড়ি কিনছে। একদিন মিলন, ইয়াসমিন আর আমি কায়সারের বাড়িতে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরি হলাম। মহা উৎসাহে যাত্রা শুরু হল। বাড়িতে কায়সারের মা আর অন্য আত্মীয়রা ছিল, কিন্তু হেনু ছিল না, সে কারণেই সম্ভবত সে আমাদের নিয়ে গেছে তার বাড়িতে। জয়দেবপুরে ছোট একটি দোতলা বাড়ি কায়সারের। তার নিজের বাড়ি নয়, তার বাপের বাড়ি। বাড়িটিতে ধন দৌলতের কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি। আমাদের নিয়ে কায়সারের কোথায় বসাই কী খাওয়াইএর ব্যস্ততা থাকার পরও মিলনের মন ভরেনি, হতাশ হয়ে বলে, ‘কী বুবু, এত না গপ্প করছিল কায়সার ভাই। ভাবছিলাম সাতমহলা বাড়ি বোধহয় তার। অহন ত দেহি ছাল উডা বাড়ি। ভাঙ্গা চেয়ার টেবিল। তার ওই গাড়িডাই আছে বেডাগিরি দেহানোর লাইগ্যা। গাড়িডা বোধহয় কিনছে খিরাজের পইসা দিয়া।’ নিজেকে ধনকুবের প্রমাণ করতে চেয়ে কায়সার যতই চেষ্টা করে সম্মান পেতে, তত সে আমাদের কাছে সম্মান হারায়। দিন দিন সে একটি হাস্যকর বস্তুতে পরিণত হয়। তার কথা, তার অঙ্গভঙ্গি সবই আমাদের বিকেলের চায়ের সঙ্গে ভাজা মুড়ির মত আনন্দ দেয়। যেন আমরা সার্কাসের জোকার দেখছি, সারাক্ষণই। তবে আমি যখন কায়সারকে নিয়ে আমার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করি, তখন তাকে আমি ভালবাসি। আমাকে সে আনন্দ দেয়। গভীর গোপন আনন্দ। পুরুষকে সুখ দেবার জন্য তাদের শরীরের তলে একটি বস্তু বা মাংসপিণ্ড হিসেবে আমি আর ব্যবহৃত হতে দিই না নিজেকে। আমার অঙ্গে কোনও জোয়ার এসেছে কি না তার খবর কোনও পুরুষই আগে নেয়নি, না নিয়েই ঝাঁপ দিয়েছে স্নান করতে। কায়সারও সে খবর নিত না, যেহেতু পুরুষের অভ্যেস নেই নেওয়ার। কিন্তু তাকে আমি বলি খবর নিতে, চাঁদ হয়ে আমাকে জোয়ার দিতে। বলি আমাকে জাগাতে, বাজাতে। শরীরের প্রতি রোমকূপ স্পর্শ করে করে শরীরকে ভালবাসতে বলি। মগ্ন হতে বলি। কায়সার হয়। আমাকে সে আনন্দ দিয়ে আনন্দ পায়। ধীরে ধীরে এমন হয় যে আমার আনন্দই প্রধান হয়ে ওঠে। আমার সুখের জন্যই সব আয়োজন। কায়সারকে আমিই ভোগ করি। আমার যখন ইচ্ছে তখন। যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে। আমার যে তাকে প্রয়োজন, এই ব্যপারটিই তাকে অহংকারী করে তোলে। কায়সার আমাকে আরও নানাভাবে আনন্দ দিতে চায়। আমাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যায়। আমার জন্য হঠাৎ হঠাৎ কিছু উপহার নিয়ে আসে। আমাকে খুশি করার জন্য সে প্রাণ ঢেলে দেয়। সাধ্য তো আছেই, সাধ্যের বাইরেও অনেক কিছু করতে সে প্রস্তুত হয়। যখন আমাকে মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বদলি করে দেওয়া হল জামালপুরে, তখন কায়সারের গাড়িতে জামালপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। মহানন্দে সে রওনা হয় আমাকে নিয়ে। জামালপুরের সিভিল সার্জন আপিসে গিয়ে চাকরিতে যোগদান করে ছুটি নিয়ে চলে আসব পরদিন, এই কথা। জামালপুরের যাত্রাটি চমৎকার যাত্রা। পথে ময়মনসিংহে থেমেছি, অবকাশে রাত কাটিয়ে পরদিন আবার জামালপুরের দিকে রওনা হয়েছি। ঢাকার ব্যস্ততা ছেড়ে দূরে কোথাও আমার এমন বেরিয়ে পড়া হয় না অনেকদিন। কায়সার গাড়ি চালাতে চালাতে আমাকে তার জীবনের অনেক কথা বলে। তার শৈশব কৈশোরের কথা। তার বাল্যকালের সঙ্গীদের কথা, খেলাধুলার কথা। শেশবগুলো আমাদের এত মেলে যে কায়সার আমার চেয়ে বছর দশেকের বড় হলেও তাকে আমার সমবয়সী বলে মনে হয়। তাকে দেখতেও বয়স কম লাগে, চপলতা তার বয়স কমিয়ে রাখে। ইট পাথরের শহর ছেড়ে ট্রাকের বাসের তীব্র চিৎকার থেকে দূরে গাছগাছালি ঘেরা মাটির বাড়িঘর দেখতে দেখতে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের জমি দেখতে দেখতে শান্ত শান্ত গ্রাম পার হই। দূরে কোথাও যেতে পারলে আমার সবসময়ই ভাল লাগে। জামালপুরের সার্কিটহাউজে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। সিভিল সার্জন দুটো ঘরের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন, বলেছি একটি ঘরেই আমাদের চলবে। প্রশ্ন করেন, উনি কি আপনার স্বামী?
না।
তাহলে দুটি ঘর..
না, একটা ঘরেই আমাদের চলবে।
আমাদের বয়স সেদিন কমে গিয়ে ষোলোয় পৌঁচেছিল! উত্তেজিত উন্মত্ত উচ্ছঅল শরীর সপ্তম আকাশেই ঘুরে বেরিয়েছে সারারাত। কায়সারকে এত আনন্দ পেতে আগে দেখিনি। আমাকে একা করে পাওয়া তার হয় না এমন। ঢাকার ব্যস্ততা থেকে বহু দূরে দুজনের কেবল দুজনের জন্য সময় কাটানোর এমন একটি সুযোগ তার জন্য স্বর্গ পাওয়া। ঢাকায় আমার সময় হয় না তেমন কায়সারকে সময় দেবার। কিন্তু যেটুকু সময়ই আমার জোটে তার জন্য, তার মন না ভরলেও আমার মন ভরে। কায়সারের সঙ্গে ঘন ঘন কদিন দেখা হয়, আবার অনেকদিনের জন্য সে উধাও, তখন মন কেমন কেমন করে। কায়সার কেবল খুঁিটনাটি খুনসুটির জন্য নয়, গভীর গম্ভীর আলোচনার জন্যও। ‘কি রে তোর কাছে কোনও চাকরি টাকরি আছে নাকি, একটা চাকরি দে তো আমার এক ফুপাতো ভাইয়ের জন্য।’ তার একটি অভ্যেস, কোনও কিছুতে কখনও সে না বলে না। তার ক্ষমতা না থাকলেও সে কথা দেবে সে চাকরির ব্যবস্থা করবে। চেষ্টা করে সে। অনেক কিছু করারই চেষ্টা করে। বেশির ভাগ কথাই সে রাখতে পারে না। ফুপাতো ভাই মোতালেব অনেকদিন বেকার বসে আছে। আমার কাছে প্রায়ই আসে একটি চাকরির জন্য। এই অভাবের অনিয়মের দেশে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করলেও চাকরি পাওয়া যায় না। কারও অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি রকম চলনসই হলেই অভাবী আত্মীয়দের ভিড় বাড়ে। কেউ আসে টাকা পয়সার সাহায্যের জন্য, কেউ চাকরি বাকরির জন্য। আমার নিজের তো ক্ষমতা নেই কাউকে চাকরি দেবার। সুতরাং আমার অনুরোধে কায়সারই রুটি বানানোর কারখানার মালিক বন্ধুকে ধরে বিএসসি পাশ মোতালেবকে একটি কাজ দিল। ছোট কাজ। তবু তো কাজ! বেকার যুবকেরা যে কোনও কাজ পেয়েই বর্তে যায়। কায়সারের এই কৃতিত্বে তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা বাড়ে। এটিই চায় সে, সে যে নিতান্তই তুচ্ছ কোনও বস্তু নয়, তারও যে কিছু হলেও ক্ষমতা আছে, সেটি সে ব্যগ্র হয়ে বোঝাতে চায়। কায়সার তার লাল গাড়িটিতে আমাকে পাশে বসিয়ে তার ধনী বন্ধুদের আপিস বা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে মুগ্ধ করতে চায়। কিন্তু সে দেখে এসব আমাকে মুগ্ধ করে না। একবার কাকরাইলের মোড়ে তার গাড়ির সঙ্গে একটি রিক্সার ধাককা লাগল, গাড়ি থামিয়ে ছুটে গিয়ে সে রিক্সাঅলাকে বেদম মার দিতে লাগল। গাড়ির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে তাকে থামতে বলেও পারি না থামাতে, শেষ পর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে মোড় ভর্তি মানুষের সামনে তাকে টেনে এনে গাড়িতে ওঠাতে হয়। কায়সার গজরাতে থাকে তার গাড়িতে দাগ পড়েছে বলে। তার অমানুষিক কাণ্ড দেখে এমনই আমার রাগ হয়েছিল যে তাকে আমি আমার বাড়িতে ঢুকতে দিইনি কয়েকদিন। ধীরে ধীরে কায়সার বোঝে যে আমি তার গায়ের শক্তি আর তার চেয়ারম্যানি শক্তিকে মোটেও পছন্দ করছি না। সে আমার পছন্দ পেতে এরপর মানবিকতার গল্প শোনাতে থাকে। জয়দেবপুরের অনেক গরিব লোক তার কাছে আসে সাহায্য পেতে এবং সে তাদের এই দিয়ে ওই দিয়ে সাহায্য করে। কায়সার আমার আড়ালে কেমন তা আমার জানা হয় না, আমার কাছে এসে তাকে মানবিক হতেই হয়। আবেগে একদিন সে কবিতা লিখতে শুরু করে। কবিতাগুলো সবই আমাকে উদ্দেশ্য করে। আমি যখন সাংবাদিক বা সাহিত্যিকদের সঙ্গে ব্যস্ত কথা বলায়, কায়সার ঘণ্টা দুঘণ্টা আমার জন্য অপেক্ষা করে আর কবিতা লেখে। কখনও ‘কিরে তুই তো ভালই লিখতে পারসঞ্চ বললে সে রঙিন হয়ে ওঠে সলজ্জ অহংকারে। লেখায় আরও মন দেয়। সেও যে লিখতে পারে, কেবল আমি নই, সেটি সে আমাকে দেখাতে চায়। জীবনে যে লোক কোনও বই পড়েনি, সে বই পড়তে শুরু করে। কায়সারের সঙ্গে আমার অতিসহজ অতিসরল অনিয়মিত কিন্তু বাঁধা সম্পর্কটি থেকে যায়। সম্পর্কটি কোনও পীড়নের সৃষ্টি করে না। সম্পর্কটি আমার সময় নষ্ট করে না। সম্পর্কটিকে জল সার দিয়ে বড় করার চেষ্টা করতে হয় না। সম্পর্কের কোনও পরিণতি নিয়ে ভাবতে হয় না। সম্পর্কটি আমার দুশ্চিন্তা ঘোচায়। পুরুষহীন-একাকীত্বের যন্ত্রণা ঘোচায়। কায়সার আমার কাছে কখনও যুবক, কখনও শিশু। কখনও সে দৃশ্যমান, কখনও সে অদৃশ্য। তবে সে যতক্ষণ আমার সামনে থাকে, সে আমার, সম্পর্ণই সে আমার। সে মানুষ কিম্বা অমানুষ সে আমার। সে শত্রু কিংবা বন্ধু, সে আমার। আমার রাগ, দুঃখ, আমার কষ্ট, সুখ সব তার ওপর বর্ষণ করতে পারি আমি। রাগ হলে ছিঁড়ে রক্তাক্ত করলাম, কষ্ট হলে কাঁদলাম, সুখ হলে হৈ চৈ করলাম, নিঃশব্দে কিন্তু সাদরে সে বরণ করে সব। কখনও তাকে বুকের কাছে নিয়ে আদর করছি, কখনও ধমকে বিদেয় করছি। কায়সার রাগ করে না কোনও চড়, ঘুষি, লাথিতে। সে জানে আবার তাকে আমি বুকে নেব। হয়ত সে বোঝে, যে, তার জন্য আমার একধরনের ভালবাসা আছে। আসলে, আছে। ভালবাসা আমার প্রিয় পুতুলটির জন্যও তো আমার আছে। বাইরের হাজার রকম কাজের পর সারা দিনের শেষে একটি নিজের কিছু সে মানুষ হোক, সে বস্তু হোক, মানুষ চায়। কায়সার আমার সেরকম। কায়সার আমাকে ভালবাসে, এটি আমাকে স্বস্তি দেয়, এটি আমাকে সুখ দেয়, আমাকে নিরাপত্তা দেয়, আমাকে মুক্তি দেয়, আমাকে ব্যস্ত হতে দেয় কাজে। কায়সারকে, আমি না অনুভব করলেও, এটা ঠিক, যে আমার ভীষণ রকম প্রয়োজন। তাকে নিয়ে আমি যে কোনও কোথাও যেতে পারি। কোনও কুণ্ঠা আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের বাড়িতে তাকে নিয়ে যাই অথবা তারা আমার বাড়িতে এসে কায়সারকে দেখে, আমাদের আড্ডায় এক কিনারে সে যখন চুপচাপ বসে থাকে। কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে না, এ কে, এর সঙ্গে কী আমার সম্পর্ক। আমি অনুমান করি যে তারা অনুমান করে নিচ্ছে সম্পর্কটি কি! এতে কারও কারও চোখ হয়ত কপালে ওঠে। কারও কপালের চোখের দিকে আমি মোটেও ফিরে তাকাই না। ফিরে না তাকালেই কপালের চোখ ধীরে ধীরে চোখের জায়গায় ফিরে আসে।
বাড়িতে বোন আছে, বোনজামাই আছে, কুলসুম আছে, এমন কী মা আছেন, আর আমি কায়সারকে আমার শোবার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করছি। কেউ এ নিয়ে কোনও কথা বলে না, এমন কী মাও নন। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলে আমি নই, মা বরং নিজেকে লুকিয়ে রাখেন অন্য ঘরে যেন মাকে দেখে আমার কোনও সংকোচ না হয়। আমার সুখে তিনি বাধা হয়ে দাঁড়ান না। মা আমাকে সুখী দেখতে চান, আমাকে তৃপ্ত দেখতে চান।
মা এত বেশি আমাকে নিয়ে ভাবেন যে আমার অর্থনৈতিক কোনও দুরবস্থা না থাকলেও তিনি আমার খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন। তিনি থাকলে তাঁর জন্য বাড়তি খাবার দরকার হয়, তাই তিনি চলে যান ময়মনসিংহে। ময়মনসিংহ থেকে চাল ডাল আনাজপাতি যখনই যা তিনি সংগ্রহ করতে পারেন, নিয়ে উদয় হন। বসে বসে দীর্ঘদিন সেই অন্ন ধ্বংস করতে তিনি রাজি নন বলে আবার উধাও হন। উধাও হওয়ার আগে অবশ্য কুলসুমকে শিখিয়ে দিয়ে যান আমাকে যত্ন করার সকল রকম পদ্ধতি। আমি কি অনেকটা বাবার মত হয়ে যাচ্ছি! বাবার মত প্রতাপ আমার। সংসার চলে আমার টাকায়, সম্পূর্ণই আমার নির্দেশে। শান্তিবাগের বাড়িতে যেমন সবাই আমাকে সমীহ করে চলে, আমার কখন কী প্রয়োজন, তা আমি না চাইতেই হাতের কাছে এগিয়ে দেয়, অবকাশের লোকেরাও বুঝে শুনে কথা বলে। বাবাও আমার দিকে আর কড়া চোখে মুখ খিঁচিয়ে তাকান না বরং তিনি আমাকে স্বর নরম করে বলেন, ‘তোমার কি কোনও পরিচিত কেউ আছে কোনও কোনও চাকরি টাকরি দেওয়ার! থাকলে মঞ্জুরে কোনও রকম একটা চাকরির যোগাড় কইরা দিও।’ মঞ্জু ঈমান কাকার ছেলে। লেখাপড়া করেনি বেশি। বাবা যেমন তার নান্দাইলের বাড়ির সবার লেখাপড়া চাকরি বাকরির দেখাশোনা করেন, আমাকেও ওরকম করতে হয় অনেকটা। খসরুকে বলে মঞ্জুকে একটি চাকরি জুটিয়ে দিই। সাভারে খসরুর জেনারেটর তৈরির কারখানা আছে, সেই কারখানায় অল্প বেতনে শ্রমিকের একটি চাকরি। আমাদের কোনও বড় বড় মামা কাকা নেই কোনও উঁচু পদে, যাদের কাছে বিপদে আপদে সাহায্যের জন্য যাওয়া যায়। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যদি কারও যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকে, সে বাবার। এরপর যতটুকু যা আছে, আমার। মঞ্জুকে আর মোতালেবকে খসরু আর কায়সারকে বলে চাকরি দুটো দিয়ে সংসারে বাবার মত একটি অবস্থান হয় আমার। কায়সারকে নিয়ে আমি অবকাশে গিয়েছি, বাবা একবারও প্রশ্ন করেননি কে এই ছেলে কী পরিচয়, কেন তার সঙ্গে আমি মিশছি। আসলে এসব প্রশ্নের অনেক উর্ধে আমি। এ কী কেবলই আমি স্বনির্ভর বলে! তা ঠিক নয়। আমি তো আরমানিটোলায় থাকাকালীনও স্বনির্ভর ছিলাম। এ তবে কী কারণে! আমি দায়িত্ববান বলে! ইয়াসমিন আর মিলনের দায়িত্ব নিয়েছি বলে! অন্তত আমার বাড়িতে তাদের থাকা খাওয়ার! নাকি আমি বড় হয়েছি বলে। অর্থাৎ বয়স হয়েছে বলে! কত আর বয়স, তিরিশও তো হয়নি। নাকি আগের চেয়ে আমার য়চ্ছলত! বেশি বলে! নাকি আমাকে বলে কোনও লাভ হয় না বলে, আমি কারও উপদেশের তোয়াককা করি না বলে! নাকি আমার নাম হয়েছে বলে! নাম তো তখনও আমার ছিল, যখন আমাকে আমার সুখের সংসার ভেঙে ঘাড় ধরে বাবা আমাকে ময়মনসিংহে নিয়ে এসেছিলেন বন্দি করার জন্য! নাকি এখন আমার বেশি নাম হয়েছে বলে! যে কারণেই হোক আমার ভাল লাগে যে আমার কোনো কাজে আমাকে কেউ বাধা দেবার নেই। স্বাধীনতার সত্যিকার স্বাদ আমি উপভোগ করি।
বন্ধু, শুভাকাঙ্খী, কবি সাহিত্যিক কেউ না কেউ আমার বাড়িতে প্রায় প্রতিদিনই আসছেন। সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি সমাজ নিয়ে ধুম আড্ডা হচ্ছে। ঘন ঘন চা পান হচ্ছে। দুপুর বা রাতের খাবার সময় হলে খাবার দেওয়া হচ্ছে টেবিলে। যার যখন ইচ্ছে খেয়ে নিচ্ছে। অতিথি আপ্যায়নেও আমি মার স্বভাব পেয়েছি। কলকাতা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এলেন, শরৎ মুখোপাধ্যায় আর বিজয়া মুখোপাধ্যায় ঢাকায় বেড়াতে এসে দেখা করে গেলেন। যে কারুকে আমি আপ্যায়ন করতে পারি, বন্ধুদের যে কেউ আমার বাড়িতে যে কদিন ইচ্ছে কাটাতে পারে, এমনই সুস্থ সুন্দর মুক্ত একটি পরিবেশ আমি ধীরে ধীরে তৈরি করে নিয়েছি। ঠিক যেরকম আমি চাই, সেরকম করে আমার সংসার, আমার জগত এবং জীবন সাজিয়েছি। আত্মীয় স্বজনের চেয়ে বন্ধুরাই আমার কাছে বেশি বড়, বেশি আপন। অবসর বলে যদি কিছু থেকে থাকে আমার, বন্ধুদের জন্যই রাখি। কালো পাহাড়ের মত মানুষটি যার মুখে কখনও হাসি ফুটতে দেখিনি সেই বাদল বসু এলেন আনন্দ থেকে নতুন প্রকাশিত বই নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য নিয়ে। বাদল বসুকে কাছ থেকে জানলে তিনি যে মোটেও বেরসিক মানুষ নন, তা বোঝা যায়। তাঁর মুখে হাসি তো ফোটেই, খুব ভাল ফোটে। ফুটলে কি হবে, আমার মুখের হাসিটি নিবে গেল যখন নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্যের পাতায় পাতায় মারাত্মক মারাত্মক ভুল দেখলাম। ‘এ কি! বইটির কি প্রুফ দেখা হয়নি!’ বাদল বসু বই ঘেঁটে বিষণ্ন মুখে বললেন, ‘সব্বনাশ হয়ে গেছে, প্রুফ দেখা হয়নি।’
‘বই বিক্রি করা তাহলে বন্ধ করুন।’
বাদল বসুর মত ডাকসাইটে লোকের মুখের ওপর বলে দিতে পারি ছাপা হওয়া পাঁচ হাজার বইয়ের বিক্রি বন্ধ করে দিতে। একটি ঝকঝকে সুন্দর পঈচ্ছদের নতুন বই হাতে নিয়ে মন ভালর বদলে মন খারাপ হয়ে থাকে। বাদল বসু বললেন ‘ছাপা যখন হয়ে গেছে তখন বিক্রি হয়ে যাক। এর পরের সংস্করণে ভুল সংশোধন করা যাবে।’ কিন্তু যে পাঠকেরা এই বইটি কিনবে তারা তো ঠকে যাচ্ছে, একটি শুদ্ধ বাক্যও পাবে না বইটিতে! ভাববে আমিই বুঝি এরকম ভুল ভাল লিখেছি। এত বড় প্রকাশনীটি নিজেদের ভুলের প্রায়শ্চিত্য করেনি, লেখকের অনুরোধের পরও বই বিক্রি বন্ধ হয়নি। বাংলাদেশের প্রকাশনীগুলো আনন্দ পাবলিশার্স থেকে অনেক ছোট। কিন্তু আমি যদি ছোট প্রকাশনীর ছোট প্রকাশকদের বলতাম প্রুফ না দেখা বই বাজারে না ছাড়তে, আমার বিশ্বাস তারা আমার কথা রাখতেন। আনন্দ আমাকে দীর্ঘদিন বিষাদে ভরিয়ে রাখে।
কিন্তু কতদিন আর বিষাদ পুষে রাখা যায়! জীবনে মনস্তাপ, সন্তাপ, বিষাদ, বিধুর, পীড়া পরিতাপের তো শেষ নেই। বিষাদকে একপাশে সরিয়ে রেখে নতুন কাজে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। চারদিকের কুৎসা রটনা, নিগ্রহ নৃশংসতা, ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতার থিকথিকে কাদার ওপর আমি জানি আমাকে মেরুদণ্ড শক্ত করে চলতে হবে, না চললে যে কোনও মুহূর্তেই আমি হোঁচট খাবো। ভেঙে যাবো। আমাকে ভেঙে ফেলার জন্য হাতে হাতে হাতুড়ি। জনপ্রিয়তার যত ভাল দিক আছে, তত মন্দ দিকও আছে। ভাল দিকগুলোর মধ্যে আমাকে আর পত্রিকা আপিসে যেতে হয় না লেখা দিতে, পত্রিকা থেকেই লেখা নিয়ে যেতে লোক পাঠানো হয়। যাই লিখি না কেন, যেমনই লিখি না কেন, ছাপা হয়। প্রকাশকরা টাকা রেখে যান বাড়িতে। জীবনে যে টাকা নিজের জন্য কখনও কল্পনা করতে পারিনি, সে সব অংকের টাকা আমার টেবিলে যে কোনও ঠোঙার কাগজের মত পড়ে থাকে। মন্দ দিক অনেক আছে। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। একাধিক বিয়ে করেছি এর অর্থ একাধিক পুরুষের সঙ্গে শুয়েছি (আমার স্বামী তালিকায় এমন অনেক লোকের নাম আছে, যাদের নাম আমি জীবনে শুনিনি)। আমি বেলাজ, বেহায়া, চরিত্রহীন। সুনীলের সঙ্গে খাতির ছিল তাই সুনীল আমাকে আনন্দ পুরস্কার দিয়েছেন (আনন্দ পুরস্কার কমিটিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন, শুনেছি তিনিই একমাত্র কমিটির সদস্য যিনি আমার পুরস্কার পাওয়ায় আপত্তি করেছিলেন)। আমি পুরুষ বিদ্বেষী। আমি ধর্ম বিদ্বেষী। আমি র এর এজেন্ট। আমার লেখা লেখা নয়, পিওর পর্নোগ্রাফি। ইত্যাদি ইত্যাদি। বন্ধু যত বাড়ে, আমার শত্রু বাড়ে দ্বিগুণ।
শত্রু বাড়ে, কতরকম মানুষ যে তবু আমার কাছে আসে! নানা বয়সের মেয়ে নানা রকম সমস্যার কথা শোনাতে আসে। এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছে তার পরিবারের লোকেরা যে ছেলেকে তার পছন্দ নয়। স্বামীর সঙ্গে অন্য মেয়ের সম্পর্ক। স্বামী মারধোর করে। স্বামী তালাক দিয়েছে। বাবা লেখাপড়া করতে দেয় না। স্বামী চাকরি করতে দেয় না। আপিসের বস শরীর চায়। যে কথা আর কাউকে বলতে পারে না, আমার কাছে বলে, দেখেছি, তারা ভারমুক্ত হয়। নিমন্ত্রণ নামে একটি উপন্যাস বেরোলো। গল্পটি ছোট, শীলা নামের এক ষোল সতেরো বছর বয়সের মেয়ে একটি সুদর্শনের যুবকের প্রেমে পড়ে। কিন্তু প্রেমে পড়লে কী হবে, সুদর্শনের মনে তো কোনও প্রেম নেই। যুবকটি একদিন নিমন্ত্রণ করে শীলাকে, শীলা ভেবেছিল যুবকটি তাকে ভালবাসে। শীলা নিমন্ত্রণে যায়, নিমন্ত্রণ না ছাই, শীলাকে একটি খালি বাড়িতে নিয়ে কয়েকটি বন্ধু মিলে ধর্ষণ করে সেই যুবক। এমন মর্মান্তিক করুণ কাহিনীটিকে লোকে বলতে লাগল অশ্লীল অশ্লীল। পড়া যায় না। ছোঁয়া যায় না। যেহেতু ধর্ষণের নৃশংস বর্ণনা দিয়েছি বইটিতে, তাই এটি অশ্লীল, তাই এটি পর্নোগ্রাফি। সমাজে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু লেখা যাবে না। লিখলে ঢি ঢি পড়ে যাবে। সমাজচ্যূত হব, একঘরে হব। লোকে আমাকে থুতু ছিটোবে। ছিটোয় থুতু। থুতু ছিটোনো যখন চলছে, এক বিকেলে অচেনা এক ভদ্রমহিলা এলেন আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ বইটি সম্পর্কে বলতে। বইটি তিনি একাধিকবার পড়েছেন এবং তাঁর দুই মেয়েকে পড়িয়েছেন। যে বইটি এমন নোংরা যে স্পর্শ করলে গা ধুতে হয়, যে বইটির অশ্লীল শব্দ পড়ে ঘেন্না হয় লোকের, সেই বইটি তিনি তাঁর কিশোরী মেয়েদের পড়িয়েছেন, তাও নাকি রীতিমত আদেশ করে! ভদ্রমহিলা বলেন, এই বইটি প্রতিটি কিশোরীর পড়া অবশ্য কর্তব্য। তিনি মনে করেন তাঁর মেয়েরা এখন অনেক বেশি সাবধানে চলাফেরা করার চেষ্টা করবে, ভুলিয়ে ভালিয়ে কেউ তাদের কোনও খালি ঘরে নিয়ে যেতে পারবে না। এই বইটি লেখার জন্য আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এরকম বই যেন আরও লিখি সেই অনুরোধ করলেন তিনি। বাইরের একশ থুতুর ছিটে ঘরের একটি ছোট্ট রুমালে মুছে নিই।
আমাকে ঢাকা থেকে সরিয়ে দেওয়ার কারণ কি? অনেকে অনুমান করেন, আমার লেখা। আমার লেখা পছন্দ হচ্ছে না কিছু কিছু সরকারি কর্তার। বিএনপির নিজস্ব পত্রিকা দৈনিক দিনকালে আপন মনের মাধুরি মিশায়ে আমাকে অপবাদ দেওয়া হয়, আমার বড় বাড় বেড়েছে, অশ্লীলতা আর অধর্মে ডুবে আমি আবোল তাবোল বকছি। আমাকে আমার জায়গা থেকে তুলে এখন দূরে কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। সাপ খোপের কামড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতেই আমার জীবন যাবে, হাতে আর কলম তোলার শক্তি পাবো না। জামালপুরের গহীন গ্রামে গিয়ে আমার চাকরি করা সম্ভব নয়, আমাকে ঢাকার কোনও জায়গায় বদলি করা হোক, ঢাকায় না হলে ঢাকার আশেপাশে হলেও চলবে এই অনুরোধ জানিয়ে লেখা আমার দরখাস্তে স্বাস্থ্য সচিব মঞ্জুরুল করিমের সই নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দিই। মঞ্জুরুল করিমের আরেকটি পরিচয় তিনি কবি, কবি ইমরান নূর। কবি বলেই সইটি দিয়েছেন তিনি। ইমরান নূরের পরামর্শে নির্মলেন্দু গুণ কিছু একটা হবে এই আশা নিয়ে আমাকে নিয়ে যান শেখ হাসিনার কাছে। আমার বিশ্বাস না হলেও নির্মলেন্দু গুণের বিশ্বাস হাসিনা চাইলে আমার বদলি পাল্টাতে সাহায্য করতে পারেন। হাসিনার সঙ্গে গুণের জানাশোনা অনেকদিনের। দুজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে পড়েছেন। হাসিনার উদ্দেশে ছাত্রাবস্থায় তিনি সম্ভবত কিছু প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন, যেমন লিখেছিলেন বিউটি কুইন পূরবী বসুকে নিয়ে।
হাসিনার মিন্টো রোডের বাসভবনে এর আগে দুবার আমি গিয়েছি। প্রথম তো রোজার সময় ইফতারির দাওয়াত খেতে, সেদিনই গুণ হাসিনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর হাসিনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল শেখ মুজিবর রহমানের জন্মদিনে ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়িতে। হাসিনা অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছিলেন। বত্রিশ নম্বর বাড়িতে ওই প্রথম আমি গিয়েছি। বুক ছিঁড়ে যায় কষ্টে যখন দেখি সিঁড়ির সেই জায়গাটি যেখানে শেখ মুজিব দাঁড়িয়েছিলেন আর বুক তাঁর গুলিতে ঝাঁঝড়া হয়ে গেল। পনেরোই আগস্ট উনিশশ পঁচাত্তর সাল। কী ভয়ংকর একটি দিন। শেখ মুজিবের পুরো পরিবারের ষোলো জনকে খুন করা হয়েছিল সেদিন। ভাল যে শেখ হাসিনা আর তাঁর বোন শেখ রেহানা দেশে ছিলেন না পনেরোই আগস্টে, তাহলেও তাঁদেরও খুন করা হত। আজ বীর দর্পে শেখ মুজিবের খুনীরা রাস্তায় হেঁটে বেড়ায়। খুনীগুলো ফ্রিডম পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলও শুরু করেছে, এর ছাত্র সংগঠনের নাম যুব কমাণ্ড। জামাতে ইসলামির মতই অবলীলায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে সারা দেশে। আজ শেখ হাসিনার মুখে আমরা শেখ মুজিবরের মুখটি দেখি। ঘোর আঁধারে একটি ক্ষীণ আলোর রশ্মি আমাদের আমাদের হৃদয়ে স্বপ্ন রচনা করে। হাসিনার সঙ্গে মিন্টো রোডে আরেকবার আমার দেখা হয়, কয়েকজন কবিকে যখন ডেকেছিলেন দুপুরের খাবার খেতে। শামসুর রাহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ শামসুল হক, বেলাল চৌধুরী আর আমি। হাসিনা অনেকক্ষণ তাঁর স্বামীর কথা বললেন, স্বামীটি যে কী নচ্ছ!র, তারই নিখুঁত বর্ণনা। স্বামী ওয়াজেদ মিয়া নাকি ফাঁক পেলেই খালেদা জিয়াকে ফোন করে রসের গপ্প মারেন। রাজনীতি বা সাহিত্য নিয়ে কোনও গভীর আলোচনায় হাসিনা যাননি। খাওয়া দাওয়া ঘর সংসার এসব বিষয় নিয়ে বেশির ভাগ সময় একাই কথা বলেছেন। আমি চুপচাপ বসে দেখছিলাম শেখ হাসিনাকে, তাঁর কথাবার্তা আমাকে মোটেও মুগ্ধ করেনি। আমি আওয়ামী লীগের কোনও সদস্য নই, কিছু নই, আওয়ামি-চক্ষু খুলে রাখি না যখন নেষনীকে দেখি। হজ্ব করে আসার পর হাসিনা কালো পট্টি বেঁধেছেন মাথায়, একটি চুলও যেন কারও নজরে না পড়ে। মেয়েদের চুলের মত অসভ্য নোংরা জিনিস যেন আর কিছু নেই, যে করেই হোক চুল ঢাকার জন্য তাই এত আকুলিবিকুলি। হাসিনার কালো পট্টির ঢং দেখলে আমার সত্যিই রাগ হয়। ধর্ম নিয়ে হাসিনা ঘরে সেদিন কোনও কথা বলেননি। ধর্ম নিয়ে বলেন বাইরে। তারপরও জানি, তাঁর দিকেই আজ তাকিয়ে আছে দেশের প্রগতিবাদী মানুষেরা। তিনিই যদি স্বাধীনতার শত্রুদের হাত থেকে, মৌলবাদীর হাত থেকে, সাম্প্রদায়িকতার কামড় থেকে দেশকে রক্ষা করেন।
শেখ হাসিনা যখন আমাদের সামনে এসে বসলেন, নির্মলেন্দু গুণই বললেন, ‘তসলিমাকে তো বদলি করে দিয়েছে, আপনি এখন ওকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করেন।’
হাসিনা বললেন, ‘আমি তো ক্ষমতায় নেই। ক্ষমতায় থাকলে সম্ভব হত। আমি তো কিছু করতে পারবো না।’
‘তারপরও দেখেন। খালেদা সরকার তো ওকে খুব ভোগাচ্ছে। পাসপোর্ট এখনও দিচ্ছে না। আর ওরকম জায়গায় বদলি..। ওর লেখালেখি ওরা পছন্দ করে না বলেই এসব করছে।’
হাসিনা শ্লেষের সঙ্গে বললেন, ‘ওর লেখা তো আমারও পছন্দ হয় না।’
নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়। গুণ ম্যাড়ম্যাড়ে কণ্ঠে বলেন, ‘কেন, পছন্দ হয় না কেন?’
‘ধর্ম সম্পর্কে ও কিছু না জেনে লেখে। ইসলামে যে নারী পুরুষের অধিকার সমান, ইসলামে মেয়েদের মর্যাদা যে সবচেয়ে বেশি —এইগুলো তো ও অস্বীকার করে।’
হাসিনা বিরোধীদলের নেত্রী। চব্বিশ ঘন্টা তাঁর ব্যস্ততা। আমাদের জন্য সামান্য সময় ব্যয় করে ব্যস্ততা অথবা অন্য যে কারণেই হোক তিনি উঠে গেলেন। যাবার আগে তাঁর দলের এক সদস্যকে বলে দিলেন, আমার ব্যপারটি দেখার জন্য। সদস্যটি টুকে নিলেন কোথায় ছিলাম, কোথায় আমাকে বদলি করেছে এ দুটো তথ্য। আমার ব্যপারটি দেখার জন্য মিন্টো রোডের কারও তেমন আগ্রহ লক্ষ করিনি।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রতিদিন খবর নিতে যাই বদলি পাল্টানোর কতটুকু কি হল অথবা আদৌ কিছু হবে কি না। দুর্ধর্ষ ডাকাতের মত চেহারার মানু নামের বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের ডাক্তার নেতার হাতে তখন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ঢাকা থেকে লোক সরিয়ে লোক ঢোকানোর। মানু আমার দিকে যেভাবে আগ্রহ নিয়ে তাকায়, তার চোখ দেখেই বুঝি সে আমাকে নামে চেনে, আমার লেখা পড়ে সে, পছন্দ করে কি করে না সে আমার জানা হয় না। মানু যে বিকেলে লিস্টিটি ফাইনাল করবে, সেদিন যেতে বলে আমাকে অধিদপ্তরে। নিরীহ প্রাণীটি গিয়ে হাজির হই আদৌ আমার যাবার কোনও প্রয়োজন আছে কী না কিছুই না জেনে। মানু একা ঘরে আমাকে নিয়ে লিস্টিটি দেখায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি খালি পদ আছে, সেই পদটিতে আমাকে ঢোকানো যায় কি না মানু ভাবছে। মানু বসে আছে, তার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আমি খুশিতে রঙিন হয়ে উঠি। কিন্তু রঙিন হওয়া মুখ ফ্যাকাসে হতে থাকে যখন কোথায় আমার পোস্টিং হবে সম্পূর্ণই তার ওপর নির্ভর করছে এই বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার দিকে পা পা করে এগোতে থাকে। সে এগোচ্ছে, আমি পিছোচ্ছি। পিছোতে পিছোতে আমি দেয়ালে। মানু আমাকে দেয়ালের কোণে বেঁধে ফেলেছে। কী তার উদ্দেশ্য! এই খালি আপিসে আমাকে সে কি ভোগ করতে চায়! ভাল জায়গায় পোস্টিং দেওয়ার লোভ দেখিয়ে! ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে তখন কাঠ নয়, লোহা হয়ে আছে। ঘৃণায় আমার থুতু ছিটোতে ইচ্ছে করে মানুর মুখে। কিন্তু থুতু ছিটোলে কী লাভ। তার উদ্দেশ্য হয়ত সে যে করেই হোক সফল করতে চাইবে! আমার চেয়ে দ্বিগুণ কেন, চতুর্গুণ বেশি শক্তি ধারণ করে সে শরীরে। তার সঙ্গে লড়াইয়ে গিয়ে আমি সফল হব না। এ মুহূর্তে একটিই পথ আছে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার, তা মানুর নাগালের বাইরে চলে যাওয়া। দেয়ালের কোণটির কাছেই দরজা। পেছনে আমার স্পর্ধা দেখে ক্রোধে দাঁতে দাঁত পেষা মানুকে ফেলে আমি দ্রুত দরজা খুলে বের হয়ে যাই। দৌড়ে পার হই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বারান্দা। দৌড়ে নিচের তলায় নামি। দৌড়ে জনতার মধ্যে। দৌড়ে রিক্সায়। বুকের ধুকপুক থামে কিন্তু চোখ জলে ভরে ওঠে অপমানে। না হয় হোক ঢাকার কোথাও চাকরি। ভাল পোস্টিংএর দরকার নেই আমার।
যৌনতার রানী আমি, আমি জরায়ুর স্বাধীনতা চাই আমার সম্পর্কে এরকম প্রচারের কোনও কমতি নেই। এতে হয়ত অনেকে ভাবে হাত বাড়ালেই বুঝি আমাকে পাওয়া যায়। না ভাবলেও ধারণা তো আছেই যে মেয়েমানুষকে দেয়ালের কোণ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলেই সাধ মেটানো যায়। কোনও ঝাড় জঙ্গলে আমাকে ছুঁড়ে দেওয়া হবে চাকরি করতে, এমন আশঙ্কার একশ পোকা নিশিদিন আমাকে কুট কুট করে কাটে। পোকার সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। পোকাময় ডাক্তারের হাতে বদলির কাগজ এল একদিন। বদলি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বিস্ময়ের ভেলা আমাকে নিয়ে আনন্দ সাগরে ভাসে।
১৮. কবন্ধের যুগ
৬ই ডিসেম্বর দুপুরবেলা আমি ঢাকা মেডিকেলের অপারেশন থিয়েটারে রোগীদের অজ্ঞান করছি। কিন্তু মন উচাটন। সেই সকাল থেকেই ভাবছি কাউকে আমার কাজের দায়িত্ব দিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ব, দুপুর পেরিয়ে গেছে তবু সুযোগ হচ্ছে না। খুব বেশিদিন হয়নি ঢাকা মেডিকেলে চাকরি করছি, এখনও কারও সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। চাকরির প্রথম দিন থেকে কাঁটায় কাঁটায় হাসপাতালে আসা, মুখ বুজে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে যাওয়া, একটির পর একটি রোগীকে অজ্ঞান করা, অপারেশনের পর জ্ঞান ফেরানো —- বিরতিহীন চলছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, বিকেলগুলো খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে সন্ধের গায়ে ঢলে পড়ে, অজ্ঞানের কাজ তখনও চলতেই থাকে। কাঁটায় কাঁটায় কাজ শুরু করলেও কাঁটায় কাঁটায় কাজ শেষ করা যায় না। শেষ কখন হবে তার ঠিক নেই। বাঁধা রোগী তো আছেই, অবাঁধা রোগীও উপচে পড়ে। ইমার্জেন্সির রোগী। এক্ষুনি এসেছে, এক্ষুনি অপারেশন না করলে বাঁচবে না জাতীয় রোগী। আটটা থেকে দুটো পর্যন্ত কাজ করে মুক্তি পাবো এমন অবস্থা নেই, বিকেলেও ডিউটি আছে, রাতেও আছে। দম ফেলার ফুরসত নেই। মিটফোর্ডে এত রোগীর অপারেশন হত না, মাঝে মাঝে একটু ফাঁক পাওয়া যেত। কিন্তু শহরের মধ্যিখানে ঢাকা মেডিকেল, এখানে ফাঁক বলে কোনও ব্যপার নেই। ঢাকা মেডিকেলে চাকরি করার সুযোগ খুব কম ডাক্তারের হয় বলে নিজের সৌভাগ্যকে আমি মোটেও ছোট করে দেখি না, দেখি না বলেই আমাকে সদা সতর্ক থাকতে হয়, ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘরে পৌঁছোনোর আগে হাসপাতালে ঢোকা চাই, পাঁচটার ঘর পেরিয়ে যদি যায় তবু বেরোনো হয় না, সে না হয় না হোক। মানুষটি আমি চেনা বলে অন্য যে কোনও ডাক্তারের চেয়েও বেশি সতর্ক থাকতে হয় আমাকে, আমার ভক্ত সংখ্যার চেয়ে অভক্ত সংখ্যা নেহাত কম নয়। লেখালেখি করি বলে নিশ্চয়ই আমি ডাক্তারিতে ফাঁকি দিই এরকম একটি অলিখিত ধারণা এই হাসপাতালটিতেও যেন চালু না হয় সেটির চেষ্টা শুরু থেকে করে আসছি। ফাঁকি যে আমি দিই না, তা প্রমাণ করতে অন্য ডাক্তারদের চেয়ে দ্বিগুণ কেন ত্রিগুণ কাজ করতে হয় আমাকে। অন্য ডাক্তাররা ঘড়ির কাঁটাকে না মেনে চললেও কথা হয় না, আমার বেলায় আমি বেশ জানি যে কথা হবে। অভিজ্ঞতাগুলো মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে অর্জন করেছি। অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করছি বলে এত সজাগ আমি, কিন্তু আজ আমাকে নিয়ম না ভাঙলেই নয়। আজ মন উচাটন। কিন্তু কার কাছে অনুমতি চাইব মুক্তি পেতে! কার কাছে প্রস্তাবটি পাড়ব! ডাক্তারদের কঠিন কঠিন মুখগুলোয় বড় নরম চোখে তাকিয়েও কোনও মুখের কাঠিন্য দূর করতে পারি না। ঘড়ি দেখছি, কিন্তু ঘড়ি দেখেই বা কী লাভ, এক রোগী টেবিল থেকে নামে তো আরেক রোগী ওঠে। অ্যানেসথেসিওলজিতে ডিপ্লোমা পাওয়া ঘন কালো মোচ আর মাথায় দলা পাকিয়ে থাকা কালো কোঁকড়া চুলের ডাক্তারটির সঙ্গে দুতিনদিন কথা হওয়ার পর মুখটি যদিও তাঁর কঠিনের কঠিন, মনটিকে খুব কঠিন বলে মনে হয়নি। মনে হয়নি বলেই তাঁকে বলি খুলে আমার আজ যে না গেলেই নয়, ফাঁকি আমার না দিলেই নয়, নিয়ম আমার না ভাঙলেই নয়। বলি যে আমার বোন হাসপাতালে, বাচ্চা হচ্ছে। বোনের বাচ্চা হচ্ছে তাতে কি! বাচ্চা সুরুৎ করে পেটে ঢোকে, ফুরুৎ করে বেরোয়। এ কারণে যেতে হয় নাকি! জানি এ কোনও যুক্তি নয় অপারেশন থিয়েটার ত্যাগ করার। তাই উচাটন মন যা নয় তাই বলে, বাড়িয়ে বলে। কণ্ঠ কাঁপে বাড়াতে গিয়ে। কোথায় তোমার বোন জিজ্ঞেস করেন তিনি। ময়মনসিংহে বললে যদি তিনি বলেন যে না অত দূর যেতে হবে না, বলি পিজিতে। ঢোক গিলে কণ্ঠের কাঁপন বন্ধ করে বলি, ‘যাবো, গিয়ে দেখেই ফিরে আসবো। এক ঘন্টাও লাগবে না।’
ডাক্তার রশীদ চুপ করে আছেন দেখে আবার বলি, এবারও বাড়িয়ে, ‘সিজারিয়ান হচ্ছে, কিন্তু বোনের নাকি অবস্থা তেমন ভাল নয়।’ কণ্ঠ এবারও কাঁপে।
চোখে কাতর অনুরোধ আমার ভাগের দায়িত্বটি তিনি যদি কিছুক্ষণের জন্য পালন করে আমাকে কৃতার্থ করেন। ডাক্তার রশীদ একবার না বলে দিলেই আমি জানি, কোনওউপায় থাকবে না আমার যাওয়ার। কালো মোচের তল থেকে বেরোলো একটি শান্তির বাণী, ‘ঠিক আছে যাও।’ বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়। দৌড়ে রাস্তায় নেমে হাতের কাছে যে রিক্সাই পেয়েছি নিয়ে সোজা শান্তিবাগ। শান্তিবাগে শান্তি নেই, কারণ কায়সার নেই। কায়সারকে বলে রেখেছিলাম সে যেন আমার বাড়িতে সকালেই চলে আসে। বেচারা এসে ঘুরে গেছে। বেচারা না হয় ঘুরে গেছে, আমি বেচারা এখন যাই কি করে ময়মনসিংহে! কায়সারের অপেক্ষা করে বসে থাকলে চলবে না, আমাকে বেরোতে হবে। বাসে বা ট্রেনে যে করেই হোক যেতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে নামছি, এমন সময় দেখি কায়সার ওপরে উঠছে। কায়সারের বাহু ধরে লাফিয়ে নিচে নামি। সোজা গাড়ি। সোজা ময়মনসিংহ। সোজা হাসপাতাল। সোজা প্রসুতি বিভাগ। ইয়াসমিন নেই। কোথায়? পোস্টঅপারেটিভ রুমে। ঠাণ্ডা হয়ে যায় শরীর। ভেবেছিলাম লেবার রুমে বাচ্চা হবে, আমি থাকব পাশে। ভেবেছিলাম ইয়াসমিনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মনে সাহস দেব। যদি কারও হাত ধরে রাখতে চায় শক্ত করে, আমার হাতদুটো দেব। কিন্তু সে সুযোগ আমার হল না। বাচ্চা হয়ে গেছে আমি এসে পৌছোনোর এক ঘণ্টা আগেই। সিজারিয়ান হয়েছে। অবস্থা আসলেই ভাল নয়। খুব চেষ্টা হয়েছিল নরমাল ডেলিভারির, সম্ভব হয়নি, ফরসেপের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু বাচ্চার অবস্থা ভেতরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছোতে থাকলে অপারেশনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সিজারিয়ানেও অনেক সময় নিয়েছে। বাচ্চার ওজন পনেরো পাউণ্ড। বাচ্চাকে ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছে। ইয়াসমিনের জ্ঞান এখনও ফেরেনি। এক হাতে রক্ত চলছে, আরেক হাতে স্যালাইন। পোস্ট অপারেটিভ রুমের পাশে বিষণ্ন দাঁড়িয়ে থাকা মিলনের কাছে শুনি সব। ভেতরে গিয়ে জ্ঞান না ফেরা ইয়াসমিনকে দেখি। কিরকম থমথমে চারদিক। কি লাভ হল দৌড়ে এসে, যদি কিছুতেই আমি থাকতে পারলাম না। এরকম আসার কি দরকার ছিল! আমি তো দূরের কোনও মানুষ নই! কথা দিয়েছিলাম আমি থাকবো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ইয়াসমিন খুব চেয়েছিল আমি যেন পাশে থাকি। থাকা হল না। মেডিকেলের এমন বিদঘুটে কড়াকড়ি না থাকলে একদিনের ছুটি নেওয়ার সাহস করতে পারতাম। নিজের ওপর রাগ হয়, কেন ছুটি নিইনি একদিনের জন্য! রাগ হয় ডাক্তার রশীদের কাছে এত কৌশল করে, যা আমি পারতপক্ষে বলি না, মিথ্যে, বলার কী দরকার ছিল! না কোনও দরকার ছিল না। দরকার ছিল আমার এখানে থাকা। হয়নি। সামান্য একটি চেনা মানুষের মত ইয়াসমিনের বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর দেখতে এসেছি। বোনের মত আসিনি। বোন না ছাই!
হাসপাতাল থেকেই ফিরে যাই ঢাকায়। রাতের ঢাকাকে কেমন যেন গুমোট লাগে। লোকজন জটলা পাকিয়ে আছে কোথাও কোথাও। মগবাজারের কাছে একটি জঙ্গী মিছিল দেখি। কেন মিছিল কিসের মিছিল কিছু বুঝতে পারি না। ট্রাফিক পুলিশ গাড়ি থামিয়ে অন্য রাস্তা ধরতে বলে। বড় রাস্তাগুলোয় গাড়ি চলতে দিচ্ছে না। গাড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে ট্রাফিকের লোককে জিজ্ঞেস করি, ‘কি হয়েছে কি? মিছিল কেন?’ কোনও উত্তর জোটে না প্রশ্নের। কায়সারকে জিজ্ঞেস করি, ‘তোর কি মনে হয়, কি হয়েছে শহরে?’ কায়সার কিছুই অনুমান করতে পারে না। আমার পক্ষেও অনুমান করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় মিছিলটি দেখে আমি বুঝতে পারি কি হয়েছে। গগন ফাটানো চিৎকার থেকে দুটো শব্দ আমি কায়ক্লেশে উদ্ধার করি, ‘বাবরি মসজিদঞ্চ। বাবরি মসজিদ নিয়ে আবারও কি হল, নব্বই সালে যেভাবে বাবরি মসজিদ ভেঙেছে খবর রটিয়ে হামলা করা হয়েছিল হিন্দুদের ওপর, এবারও কি তেমন হচ্ছে নাকি!
আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে যায় কায়সার। আমি টেলিভিশন খুলে বসি। সিএনএন খুলতেই দেখি ভয়ংকর দৃশ্য। বাবরি মসজিদের ওপর ঝাাঁপিয়ে পড়ছে গেরুয়াপোশাক পরা হিন্দু মৌলবাদীরা। খবরে বলছে, বাবরি মসজিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বুকের দেয়াল কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে দিল, আর স্রোতের মত দরজা জানালা সজোরে খুলে বেরিয়ে এল হৃদপিণ্ডের সব রক্ত। কী হবে এখন? কি হবে এখন তা অনুমান করার সাধ্য আমার নেই। এই হল আমার ছয়ই ডিসেম্বরের রোজনামচা।
তারপর সাতই ডিসেম্বর। সাতের পর আসবে আটই ডিসেম্বর। তারপর নয়। দশ। কেমন সেই দিনগুলি! দিনগুলি কেমন তা ভাল গল্পকার হলে নিখূঁত বর্ণনা করতে পারতাম। কিন্তু আমি ভাল গল্পকার নই। আমি কেবল ভেতরে অনুভব করি, বোঝাতে পারি না। সাতই ডিসেম্বর তারিখে সকালে সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পাতা জুড়ে বড় একটিই খবর, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, বিধ্বস্ত। নব্বইএর অক্টোবরে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়নি, তখনই ইনকিলাবের একটি ভুল খবরের কারণে দেখেছি পুরোনো ঢাকায় কি করে হিন্দুদের মন্দিরগুলো ভেঙে চুরমার করা হয়েছে, হিন্দুদের বাড়িগুলো, দোকানগুলো লুঠ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেদিনও আমি ময়মনসিংহ থেকে রাতে ফিরেছিলাম ঢাকায়। আরমানিটোলায় থাকি তখন, সারারাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাঙনের শব্দ শুনেছি। চিৎকার আর কান্নার শব্দ সারা রাত। বাড়িঘরে মন্দিরে দোকানপাটে লাগানো আগুন লক লক করে বাড়তে বাড়তে আকাশে উঠল, দেখেছি। দেখেছি আর বেদনায় হতাশায় ক্রোধে ক্ষোভে একা একাই ফেটে পড়েছি। আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না কোথাও গিয়ে কিছু থামাই। থামাই কোনও মর্মঘাতি করুণ বিনাশ। পরদিন হাসপাতালে যাওয়ার পথে দেখেছি ভাঙা পোড়া দালানকোঠো। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শাঁখারি বাজার, সুত্রাপুর, নবাবপুর, নয়াবাজার, বাবু বাজার, ইসলামপুর, ঠাঁটারি বাজার, সদরঘাট ঘুরে ঘুরে অগুনতি পোড়া বাড়িঘর, দোকানপাট, মন্দির দেখতে দেখতে আমি হতবুদ্ধি বসেছিলাম। পুড়ে যাওয়া ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। আমি কোনও নাম দিতে পারি নি ওই বর্বরতার। মানুষ কি করে পারে জন্ম থেকে দেখা প্রতিবেশির ঘরে আগুন দিতে! কী করে পারে এমন ধ্বংসের খেলা খেলতে! কী করে পারে পাশের দোকানটি লুঠ করে, যে দোকানের আয়ে সংসার চালাতো দোকানের লোকটি, ভেঙে দিতে, পুড়িয়ে দিতে! নৃশংসতার একটা সীমা আছে, সীমা কেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে এ দেশের মানুষ! কি ঢুকেছে মানুষের মগজে! এ দেশের হিন্দুরা বাবরি মসজিদ কোথায়, মসজিদটি কেমন দেখতে তাও তো জানে না, কী করে ভাঙবে তারা সেই মসজিদ! যদি না ই ভাঙে, তবে কেন মসজিদ ভাঙার দোষ পরে তাদের ওপর! পোড়া ভিটের ওপর মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা উন্মুল উদ্বাস্তু মানুষের কান্না কেবল দেখেছিই, কিছুই করতে পারিনি। কি করে সাহায্য করব আমি দুর্গতদের! আমার সে সাধ্য ছিল না। গোপনে কেবল চোখের জল ফেলেছি।
মিথ্যে খবরেই যদি ওরকম কাণ্ড ঘটতে পারে, তবে আজ সত্যি সত্যিই যখন হিন্দু মৌলবাদীরা ভেঙে গুঁিড়য়ে দিয়েছে বাবরি মসজিদ, কি হবে আজ! আশঙ্কা আমাকে জ্বালিয়ে মারে। সকালে হাসপাতালে যাওয়ার পথে দেখি মালিবাগের জলখাবার পুড়ছে, রাস্তায় ছড়িয়ে আছে দোকানের চেয়ার টেবিল, ভাঙা। জলখাবারে আমি অনেকদিন খেয়েছি। বাড়িতে নাস্তার আয়োজন যেদিন না হত, অথবা মন খুব খুশি খুশি, ভাল কিছু খেতে ইচ্ছে হত, জলখাবারে চলে যেতাম খেতে, নয়ত ঠোঙায় করে বাড়ি নিয়ে আসতাম লুচি, নিরামিশ, হালুয়া। পথে আরও দোকান দেখি পুড়ে ছাই হয়ে আছে। লুঠ হওয়া, ভাঙা পোড়া দোকানগুলো দেখে বুঝি যে ওগুলো হিন্দুর দোকান ছিল। কোন দোকানটি হিন্দুর, কোনটি মুসলমানের তার খবর আমি বা আমার মত অনেকে না রাখলেও কেউ কেউ রাখত। হাসপাতালে পৌঁছে অপারেশন থিয়েটারে নিঃশব্দে গিয়ে নিঃশব্দে অজ্ঞান করতে থাকি রোগীদের। আশঙ্কা আমাকে ছেড়ে এক পা কোথাও যাচ্ছে না। কি হয় কি হয় কি জানি কি হয় আশঙ্কা। এখনও কি সরকার কোনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে না হিন্দুদের! যদি না করে থাকে! শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি ঘেমে উঠি।
দুপুরের দিকে ডক্টরস ক্যান্টিনে চা খেতে গিয়ে শুনি বলাবলি হচ্ছে, ইমারজেন্সিতে ক্যাসুয়ালটির রোগীর ভিড় হচ্ছে খুব, সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। আচমকা একটি আশঙ্কা ঝড়ের ঝাপটা দিয়ে আমার হাত কাঁপিয়ে কাপ নাড়িয়ে জিভ পুড়িয়ে দেয় গরম চায়ে। চা পান শেষ হয় না। ছুটি ইমারজেন্সিতে। মাথা ফাটা, পা কাটা, পিঠ ভাঙা রোগীর ভিড়। স্ট্রেচারে করে রোগী ঢোকানো হচ্ছে রুমে। রুমে জায়গা হচ্ছে না, বারান্দায় রাখতে হচ্ছে রোগীদের। বারান্দার কয়েকজন রোগীর নাম জেনে নিই, বিশ্বনাথ, সুধীর, গোপাল, করুণা, পার্বতী। ইমারজেন্সি রুমে ঢুকে তিনজন ডাক্তারদের একজনকে বলি, ‘এখানে তো আরও ডাক্তার লাগবে, এত পেশেন্ট কি করে ম্যানেজ করবেন!’ ডাক্তার বললেন, ‘কি আর করা যাবে! এক্সট্রা ডাক্তার তো আর পাওয়া যাবে না এখানে। সবারই তো ডিউটি আছে।’
‘ওটিতে আমার দুটো পেশেন্ট বাকি আছে, সেরে আমি চলে আসছি এখানে।’ আমি দ্রুত চলে যাই দোতলায়। বাকি দুটো রোগীকে অজ্ঞান করি, জ্ঞান ফেরাই। ততক্ষণে ইমারজেন্সি থেকে সার্জারি ওয়ার্ডে হয়ে নতুন রোগী আসতে শুরু করেছে অপারেশন থিয়েটারে। অ্যানেসথেসিয়া দিতে বিকেলের ডিউটির ডাক্তার এসে গেছেন অপারেশন থিয়েটারে। আমার বিদায় নেবার পালা। বলি একা সামাল দিতে না পারলে, আমি ইমারজেন্সিতে আছি, আমাকে যেন তিনি ডেকে পাঠান। ইমারজেন্সিতে আগের চেয়ে রোগীর ভিড় এখন আরও বেশি। বাড়তি ডাক্তার হয়ে রোগীর চিকিৎসা করতে থাকি। হাতে হাতে স্যালাইন দিতে থাকি, রক্ত লাগবে, দৌড়ে যাচ্ছি রক্ত আনতে। কারও গায়ে কুড়ুলের কোপ, কারও মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে, কেউ মাথায় লাঠি বা কিছুর আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কেউ গুলিবিদ্ধ, কারও মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে মারের চোটে। সন্ধে হতে থাকে, রোগীর ভিড় আরও বেশি বাড়ে। ডাক্তারদের দম ফেলার সময় নেই। ঘড়ির দিকে তাকাবো, সে সময়ও নেই আমার। সারাদিন না খাওয়া, ক্যান্টিনে গিয়ে যে চা সিঙ্গারা খেয়ে আসবো, সে সময়ও পাওয়া হয় না। অপারেশন থিয়েটারেও রোগী নিয়ে যেতে হয়, ওখানে অ্যানেসথেসিয়া দিতে বাড়তি ডাক্তার হিসেবে কাজে লেগে যাই। অপারেশন করতে করতে সার্জন বলছেন, আজ সারারাতই রায়টের রোগী আসবে।
‘রায়টের? রায়ট কোথায় বাঁধলো?’ আমি প্রশ্ন করি।
‘দেখছেন না! সব তো রায়টের রোগি আসছে ইমারজেন্সিতে।’
‘কিন্তু সব তো হিন্দু! রায়ট হলে তো কিছু মুসলমানও পাওয়া যেত। হিন্দুতে হিন্দুতে তো কোনও মারামারি বাঁধেনি। মুসলমানরা হিন্দুদের মারছে।’
সার্জন কোনও কথা বলেন না।
যখন হাসপাতাল থেকে বেরোই, রাত দশটা বাজে। বাড়ি পৌঁছে ক্লান্ত আমি আজকের কাগজের শিরোনামগুলোয় চোখ বুলোই শুধু। উগ্র হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে বাবরি মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত। উত্তর প্রদেশ সরকার ও রাজ্যসভা বাতিল। ভারতে প্রতিবাদের ঝড়। সমগ্র ভারতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার। মসজিদ প্রাঙ্গণে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্টের ২৪ ঘণ্টা বনধ। বাবরি মসজিদ ঘটনায় বাংলাদেশের উদ্বেগ প্রকাশ। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ। হাসিনার নিন্দা ও প্রতিবাদ। পাঁচ দলের নিন্দা ও প্রতিবাদ। সিপিবির নিন্দা। হিন্দু সাধুদের মন্দির নির্মাণের প্রচেষ্টাঃ নয়া রাজনৈতিক সংকটে রাও সরকার।
পরদিন আটই ডিসেম্বর, ভোরবেলা উঠে উঠে চা খেতে খেতে পত্রিকার খবরগুলো দেখি, বাবরিমসজিদ ভেঙে ফেলার পর অশান্ত ভারতে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। হত দুশতাধিক, আহত কয়েক হাজার। আরএসএস শিবসেনাসহ মৌলবাদী সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ। লোকসভার বিরোধী নেতার পদ থেকে আদভানীর পদত্যাগ। বর্তমান স্থানেই মসজিদটি আবার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত। বাবরি মসজিদ হামলার প্রতিবাদে ও ৪ দফা দাবিতে সমন্বয় কমিটির আহবানে আজ সারাদেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল। শান্তি ভাঙার চেষ্টার পরিণাম শুভ হবে না। বাবরি মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর সংঘর্ষ। আহত তিন শতাধিক। ২৫ জন বুলেট বিদ্ধ। যে কোনও মুল্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখুন–শেখ হাসিনা। মন্ত্রি পরিষদের বিশেষ বৈঠক—দেশবাসীকে শান্ত থাকার আহবান। বাববি মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে জামাত শিবির বিভিন্ন মন্দির ভাঙচুর লুটপাট অগ্নিসংযোগ করেছেঃ পরিস্থিতি উত্তেজনাকর। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আহবান জানাচ্ছে বামদলগুলো। পুরো খবর পড়ার সময় নেই, হাসপাতালে দৌড়োতে হয়। আজ সারা দেশে হরতাল হচ্ছে বাবরি মসজিদে হামলার প্রতিবাদে। হরতাল, কিন্তু কিছু রিক্সা চলছে, শান্তিবাগ থেকে হেঁটে মালিবাগে এসে একটি রিক্সা নিই, এত সকালে পিকেটাররা রাস্তায় নামেনি বলে চলে যেতে পারি অনায়াসে। হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে গতকালের চেয়ে আজকে বেশি ভিড় মার খাওয়া গুলি খাওয়া কোপ খাওয়া ছুরি খাওয়া পুড়ে যাওয়া মানুষের। হরতালের মধ্যেও ভিড়ের কোনও কমতি নেই। মানুষ আসছে পায়ে হেঁটে, রোগী কাঁধে নিয়ে। আজও অপারেশন থিয়েটারের কাজ শেষ করে ইমারজেন্সিতে ঢুকে যাই। এক একজন মানুষ, এক একটি গল্প। এক একটি জীবন। যাদের কথা বলার মত অবস্থা আছে, জিজ্ঞেস করে জেনে নিই কিকরে আক্রমণ হয়েছে তাদের ওপর। কি করে নিরীহ মানুষগুলোর ওপর সন্ত্রাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আচমকা লাঠি হাতে, কুড়ুল হাতে, ছুরি হাতে। সুবোধ মণ্ডলের হুঁশ ছিল না কথা বলার। কাতরাচ্ছিল লোকটি। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে মাথা থেকে, কুড়ুলের কোপে মাথার খুলি কেটে ঢুকে গেছে ভেতরে।
‘কারা এই অবস্থা করেছে, কারা?’ সুবোধ মণ্ডলের মাথার ক্ষত এন্টিসেপটিক দিয়ে মুছে ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে দ্রুত একটি এন্টিটিটেনাস ইনজেকশান দিয়ে দুই হাতে স্যালাইন আর রক্ত চালিয়ে নাকে অক্সিজেন দিয়ে স্ট্রেচারে তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করি। পাশে দাঁড়িয়ে আছে সুবোধের স্ত্রী গায়ত্রী।
‘কারা ওরা? চেনেন?’ বিন্দু বিন্দু ঘাম আমার কপালে।
গায়ত্রী বলল, ‘চিনুম না কেন, ওরা তো আমাগো পাড়ার লোকই, আবুল, রফিক, হালিম, শহিদুল।’
‘কেন মারলো আপনাদের? কি অভিযোগ করল?’
গায়ত্রী গলা চেপে ‘কইল আমরা নাকি মসজিদ ভাঙছি।’ বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আমার হাতদুটো চেপে ধরে বলতে থাকে ‘দিদিগো, আমরা কোনও মসজিদ ভাঙ্গি নাই। বিশ্বাস করেন দিদি, মা কালির দিব্যি দিয়া কইতাছি আমরা ভাঙ্গি নাই।’
‘কোন মসজিদ ভাঙার কথা কইছে, জানেন?’
‘কী জানি কোন মসজিদ! জানি না। রিক্সা কইরা যখন আইতাছি সীতার বাপরে লইয়া, তখন ত অনেকগুলা মসজিদ দেখলাম, কোনওটাই তো ভাঙ্গা দেখলাম না।’
‘বাবরি মসজিদের নাম শুনেন নাই?’
গায়ত্রী মাথা নাড়ে। নাম শোনেনি।
বাবরি মসজিদ কোথায় তা জানে কি না জিজ্ঞেস করি, গায়ত্রী জানে না। গায়ত্রীর একটিই জোড় হাত প্রার্থণা, তার স্বামীকে যেন বাঁচিয়ে তুলি। স্বামী তার বাবুবাজারে আলু তরকারি বিক্রি করে। স্বামী না বেঁচে উঠলে দুটো ছেলে মেয়ে নিয়ে গায়ত্রীর উপোস করে মরতে হবে। ডাক্তাররা চেষ্টা করেও পারেননি গায়ত্রীর স্বামীকে বাঁচাতে। আমার চোখের সামনে গায়ত্রী তার স্বামীর দেহটি নিয়ে বারান্দায় নিথর বসে রইল। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেনি। আরও রোগী আসছে, বারান্দা খালি করে দিতে হয়েছে গায়ত্রীকে।
রোগীদের কাউকে কাউকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দিচ্ছি, কাউকে মেডিসিন ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কাউকে সার্জারি ওয়ার্ডে। ব্লাড ব্যাংক থেকে এনে রক্ত চালু করে দিচ্ছি। সব ওষুধ হাসপাতালে নেই, গরিব রোগীদের আত্মীয় স্বজনের কাছে টাকা পয়সাও নেই। অ্যাপ্রোনের পকেটে যে কটা টাকা ছিল, ঝেড়ে দিয়ে দিই দুতিনজন গরিবকে ওষুধ কিনে আনতে। সন্ধানীতে গিয়ে বিনে পয়সার ওষুধ মুঠো ভরে ভরে নিয়ে এসে যাদের ওষুধ কেনার পয়সা নেই, দিই। রোগীদের কাছে কি করে কি হল তার বর্ণনা শোনার সময় নেই আমার। আমার জানা হয়ে গেছে কি করে হয়েছে এইসব কাণ্ড। আমার আর জানার দরকার নেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোন কোন মন্ত্রী কি কি সব চমৎকার চমৎকার কথা বলছেন। জানার দরকার নেই খালেদা কি বলছেন, হাসিনা কি বলছেন, বা তাঁদের দলই বা কি করছে। রাজনীতির মুখে মনে হয় মানুষের গা থেকে ঝরতে থাকা রক্ত লেপে দিই। আজ আমার ডিউটি রাতে, রাতের ডিউটি শুরু হয় আটটা থেকে। ডিউটি থাকলে সাধারণত দুপুরে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে রাত আটটায় চলে আসি হাসপাতালে। আজ আমার আর বাড়ি যাওয়া হয়নি। সেই সকাল আটটা থেকে কাজ শুরু করেছি, বিকেল শেষ হয়েছে, রাত নেমে এসেছে, সারারাত কখন কেটে গেছে টের পাইনি। সারা রাতই বানের জলের মত রোগী এসেছে, সারা রাতই ইমারজেন্সির ডাক্তারদের হিমশিম খেতে হয়েছে। ভোরবেলায় ইমারজেন্সির এক অচেনা ডাক্তার আমাকে প্রশ্ন করে, ‘আপনি কি হিন্দু?’ ইমারজেন্সিতে আমার ডিউটি নেই, কিন্তু তারপরও এখানে বাড়তি কাজ করছি, রোগীদের বাঁচাবার চেষ্টা করছি, আমি নিশ্চয়ই হিন্দু, তাই আমার এত আবেগ, ডাক্তারের ধারণা।
ডাক্তারটির প্রশ্নের আমি প্রথম আমি কোনও জবাব দিইনি। পরে আবার যখন জিজ্ঞেস করল, তখন দাঁতে দাঁত চেপে বলি, আমি মানুষ।
রাতে ডিউটি থাকলে পরদিন ছুটি থাকে। ক্লান্ত শরীর আর বিধ্বস্ত মন নিয়ে সকালে ফিরে আসি বাড়িতে। বাবরি মসজিদে হামলার নিন্দা আর প্রতিবাদ চলছে সারা দেশে। সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহবান জানানো হচ্ছে। সম্প্রীতি রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছে বাম দলগুলো। আওয়ামি লীগ থেকেও বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্থান নেই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালিত হতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। ছাত্র সংগঠনগুলো আজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য শান্তি মিছিল করবে শহরে। হচ্ছে অনেক কিছুই, তারপরও হিন্দুর ওপর নির্যাতন চলছেই সারা দেশে। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে আমার, খেয়ে একটু ঘুমোবো আশা করেছিলাম। খাওয়া হয়, ঘুম হয় না। বেরিয়ে পড়ি রিক্সা নিয়ে। রিক্সা শান্তিনগর পার হয়ে পল্টনের দিকে যায়, পল্টন থেকে মতিঝিলের দিকে যেতে যেতে দেখি কমিউনিস্ট পার্টির অফিস পুড়ে ছাই হয়ে আছে, আরেকটু এগোলে শাপলা চত্ত্বরের কাছে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিসটিও পোড়া। রাস্তায় ইট পাটকেল, পোড়া কাঠ পড়ে আছে। আরও দোকানপাট ভাঙা, পোড়া। পুরোনো ঢাকার দিকে গেলে ওখানে আরও দেখতে পাবো বাড়িঘর জ্বলছে পুড়ছে। যাবো! দেখবো! কিন্তু দেখে কী লাভ! জানিই তো কি হচ্ছে দেশে! কি দরকার আর আহত নিহত মানুষ আর ভাঙা পোড়া বাড়ি আর মন্দির দেখে! বড় একটি মিছিল চলে গেল টুপিওয়ালাদের, ‘বাবরি মসজিদ ধ্বংস কেন, ভারত সরকার জবাব দাওঞ্চ বলে চিৎকার করতে করতে। এরাই নিশ্চয়ই বাড়িঘরে মন্দিরে দোকানপাটে আগুন ধরাচ্ছে, এরাই নিশ্চয়ই যেখানে যে হিন্দু পাচ্ছে আক্রমণ করছে। এই লোকগুলোকে আমার মানুষ বলে মনে হয় না। মানুষের রূপ ধরে যেন এক একটি মানুষখেকো জন্তু। রিক্সাকে পলাশির দিকে যেতে বলি। পলাশির বস্তিতে নেমে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে বস্তির যে ঘরটিতে নির্মলেন্দু গুণ থাকেন, সেটির দরজায় টোকা দিই। ঘরের দরজাটি নড়বড়ে। কেউ একটি লাথি দিলেই ভেঙে পড়ে যাবে দরজা। রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে মলিন ঘরটি। আমার ভয় হয়, এই ঘরটিও সম্ভবত পুড়িয়ে দেবে। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি নির্মলেন্দু গুণকে যে কোনও মুহূর্তে হয়ত পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে। গুণ ঘরে ছিলেন, বিছানার ওপর পা তুলে বসে আছেন। আমি বিছানায় বসে গুণের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারিনি। কেন এসেছি আমি! সান্ত্বনা দিতে! কি বলে সান্ত্বনা দেব গুণকে! রাস্তায় চিৎকার করছে একপাল ছেলে, ‘একটা দুইটা হিন্দু ধর, সকাল বিকাল নাস্তা কর।’ চিৎকারের শব্দ কমে এলে গুণ বললেন, ‘পা নামাই না বিছানা থেকে, মনে হয় পা নামাইলেই বুঝি ওরা ধইরা ফেলবে।’ রসবোধ গুণের খুব বেশি। এই ভয়ংকর দুর্যোগের সময়েও তিনি লোক হাসাতে চান। আসলে কি হাসাতে চান নাকি এটি গুণের মনের কথা! মাটিতে পা রাখতে আসলেই তাঁর ভয় হয়! আমার বিশ্বাস, হয়। নির্মলেন্দু গুণের মত কিছুকে পরোয়া না করা শক্ত সমর্থ সাহসী মানুষটির চোখে আমি থোকা থোকা অনিশ্চয়তা আর আতঙ্ক দেখতে পাই, যতই তিনি তা লুকোনোর চেষ্টা করুন না কেন। এই সমাজে মেয়েদের কোনও নিরাপত্তা নেই, তারপরও আজ আমি নিরাপদ বোধ করছি, যেহেতু আমার নামটি মুসলমান নাম। আর দেশের বড় কবি হয়েও, পুরুষ হয়েও, সাহসী হয়েও, রাজনীতিবিদ হয়েও নির্মলেন্দু গুণ নিরাপদ বোধ করছেন না। আমার চেয়েও এখন অনেক অসহায় তিনি।
‘গুণদা, আমার বাসায় চলেন।’ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বাক্যটি বেরিয়ে আসে।
না তিনি যাবেন না। বাড়িভর্তি গুণের পোষ্য, গীতাসহ গীতার কয়েকটি বোন। তিনি সবাইকে ছেড়ে একা নিজের জন্য নিরাপত্তা নেবেন না।
অসীম সাহা কেমন আছেন, মহাদেব সাহা কেমন আছেন, জিজ্ঞেস করি। গুণ জানেন না কে কেমন আছেন। তিনি কেবল জানেন যে তিনি বেঁচে আছেন, এই বেঁচে থাকার কারণটি সম্ভবত, তাঁর ধারণা, দেখতে তাঁকে মুসলমান মৌলবির মত লাগে। লম্বা দাড়িঅলা, পাজামা পাঞ্জাবি পরা মানুষটি মৌলবী না হয়ে যান না, বস্তির লোকদের এমনই ধারণা। কিন্তু এভাবে কিছু লোকের চোখ হয়ত ফাঁকি দেওয়া যায়, সব লোকের চোখ নয়। ঘরের মেঝেয় বসে আছে চারবছর বয়সী একটি বাচ্চা ছেলে, ছেলেটি গীতার বোন কল্যাণীর পুত্রধন। কল্যাণীর বিয়ে হয়েছিল এক মুসলমান লোকের সঙ্গে, তখন সুমন জন্মায়। সুমনকে দেখিয়ে গুণ বলেন, ‘ও তো হাফ মুসলমান। ও আছে বলেই আমরা সবাই ভরসা পাই। সুমনরে বলছি এই ঘরে বইসা থাকতে। কেউ যদি আত্রমণ করতে আসে, সোজা বলে দেব যে এই বাড়িতে একজন মুসলমান আছে, সুতরাং সাবধান, কোনও রকম আক্রমণ যেন না হয়।’
আমি হেসে উঠি। নির্মলেন্দু গুণ হাসেন না। মনে হয় তিনি সত্যিই মনে করছেন, চার বছরের মুসলমান বাচ্চাটির কারণে তিনি বাঁচবেন, গীতা আর গীতার আত্মীয়রা বাঁচবে। গুণ বললেন, ‘সুমনকে তো এখন ভাল খাওয়ানো দাওয়ানো হচ্ছে। বেশ আদর যত্ন করা হচ্ছে। ও হইল আমাদের সবার রক্ষাকর্তা। সুমনও বুইঝা গেছে সেইটা। আমারেও মাঝে মাঝে ধমক দিয়া কথা বলে।’
আমি জোরে হেসে উঠি। গুণ গম্ভীর হয়ে বলেন, ‘ভাবছি অসীম কেমন আছে তা দেখতে ওর বাসায় যাবো একবার। সুমনকে নেবো। সুমনে আগে আগে হাঁটবে, আমি সুমনের পেছন পেছন। সঙ্গে একজন মুসলমান থাকলে ভয় ডর কম থাকবে।’
এবার আমার আর হাসি পায় না। মাথায় একটি চিনচিনে যন্ত্রণা টের পাই। একটি বিচ্ছিরি রকম অসহায়বোধ আমাকে ছাড়পোকার মত কামড়াতে থাকে। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি, সেই সঙ্গে গুণকেও। বলতে থাকি, কাল সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে মানববন্ধন হচ্ছে। বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে সংসদ ভবন পর্যন্ত লম্বা। আওয়ামি লীগ শান্তিমিছিল বের করবে। বিএনপিও করবে। আজও তো ছাত্রঐক্যের শান্তিমিছিল হচ্ছে। জামাত শিবিরকে যে কোনও ভাবে ঠেকানোর চেষ্টা চলছে। গুণ শোনেন। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই তাঁর। সাধারণত রাজনীতির প্রসঙ্গে গুণ মুখর হয়ে ওঠেন। আজ সব মুখরতা আকাশের ওপারে চলে গেছে। জিজ্ঞেস করি কোনও পত্রিকা তিনি পড়ছেন কি না। না, কোনও পত্রিকাই তিনি পড়ছেন না, টেলিভিশনও দেখছেন না। তিনি কিছুই করছেন না। শুধু বসে থাকছেন বিছানার ওপর। খাবার খাচ্ছেন বিছানায় বসে, পেচ্ছ!ব পায়খানায় যেতে হলে দৌড়ে যাচ্ছেন, সেরে দৌড়ে এসে আবার বিছানার ওপর উঠে গুটিসুটি বসে থাকছেন। রাতে ঘুমোন না, বসে থাকেন। শুতে ভয় করে, শুলে যদি ঘুম এসে যায়, আর ঘুমোলে যদি ঘুমের মধ্যে কেউ মেরে রেখে যায়! ঘুমোন না, কারণ ঘুমিয়ে থাকলে চার বছরের মুসলমান বাচ্চাটির দায় দায়িত্ব যে তিনি নিয়েছেন, তা ব্যাখ্যা করে বেঁচে থাকার যদি একটি সুযোগ পাওয়া যায়, সেই সুযোগটি কেন হারাবেন! একটি ন্যাংটো বাচ্চা, নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে, গা ধুলোয় মাখা, অথচ এই বাচ্চাটিকেই এ বাড়ির সবার চেয়ে শক্তিমান মনে করছেন নির্মলেন্দু গুণ। আমারও হঠাৎ মনে হয়, সুমনই এ বাড়ির গায়ে গতরে শক্তিধর, মেধায় বুদ্ধিতে শক্তিধর যে কোনও প্রাপ্ত বয়স্কদের চেয়েও বেশি শক্তি ধারণ করছে। সুমনই এ বাড়িতে সবচেয়ে মূল্যবান একটি প্রাণী।
বিষাদ আমাকে আচ্ছত করে রাখে যখন বেরোই গুণের বাড়ি থেকে। বেরিয়ে অসীম সাহার বাড়িতে যাই, মহাদেব সাহার বাড়িতেও। গুণের মত ভাঙা ঘরে তাঁরা থাকেন না।কিন্তু ভয় একই রকম সবার। নিস্তেজ পড়ে আছেন, সর্বাঙ্গে আতঙ্ক। দরজায় শক্ত করে খিল এঁটে বড় বড় ছেলে মেয়ে নিয়ে বসে আছেন ঘরে। কবে বাইরে বেরোবেন, আদৌ বেরোতে পারবেন কি না কিছুই জানেন না। অসীম সাহার ইত্যাদি প্রেসটি বন্ধ। মহাদেব সাহা ইত্তেফাকে চাকরি করেন, এখন আর চাকরি করতে যাচ্ছেন না। আমি কাউকে কোনও সান্ত্বনার বাণী শোনাতে পারি না। আগামীকাল মানববন্ধন হচ্ছে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, এই সংবাদ কারও আতঙ্ক দূর করে না। বাড়ি ফিরে আসার পথে আমি ভাবি, দেশের বড় বড় কবিদেরই যদি আজ এমন করে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকতে হয়, তবে সাধারণ হিন্দুরা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে এ দেশে! নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, অসীম সাহা সকলেই আপাদমস্তক নাস্তিক। আজ তাঁদেরকেও ভয়ে গুটিয়ে থাকতে হচ্ছে, যেহেতু তাঁরা হিন্দু নাম ধারণ করে আছেন। আমার নামটিও হিন্দু নাম হতে পারত, আমার জন্মও হতে পারতো কোনও হিন্দুর ঘরে। কি হত আমার তবে আজ! আমি কি পারতাম রাস্তায় বেরোতে! হয়ত ধর্ষিতা হতে হত। হয়ত পুড়িয়ে ফেলা হত আমাকে, আমার বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হত, আমাকে সর্বস্বান্ত করা হত!
দশ তারিখে সকাল সকাল হাসপাতাল পৌঁছোই। তখন রোগী আনা হয়নি অপারেশন থিয়েটারে। ক্যান্টিনে চা সিঙ্গারা খেতে খেতে দেখি টেবিলের ওপর পড়ে আছে দুদিন আগের ইনকিলাব পত্রিকাটি। ব্যানার হেডলাইন, বাবরি মসজিদের স্থানে হিন্দু মন্দির নির্মাণ, উগ্র হিন্দুদের উল্লাস, আহত ১০০০ নিহত দুই শতাধিক। পত্রিকাটি আলগোছে উল্টো রেখে দিই। এই পত্রিকাটি হিন্দুর ওপর হামলা করার জন্য এ দেশে মহান ভুমিকা রাখছে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। পাশের টেবিলে কজন ডাক্তারের আলোচনা কানে আসে,ভারতে বিজেপির সভাপতি যোশি আর আদভানীসহ মোট আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মূল্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংএর বিচারের দাবি উঠেছে। উগ্রবাদী সাতশ হিন্দুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লোকসভা বিধানসভা স্থগিত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর এসএস, বজরং দল, জামাতে ইসলামি দলগুলোকে ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ দেশে কি হচ্ছে? হিন্দুর বাড়িঘরে মন্দিরে দোকানপাটে লুটতরাজ চলছে, আগুন লাগানো চলছে। হিন্দুর জমি জমা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ গ্রেফতার করেছে বেশ কিছুজনকে। কোথাও কোথাও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। বাম দল, আওয়ামি লীগ, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ঘোষণা দিচ্ছে, বিবৃতি দিচ্ছে, বৈঠক করছে, মিছিল করছে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিগুলোকে এক হতে বলা হচ্ছে। জামাত শিবিরকে মূলত দোষী করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর জন্য। বাংলাদেশ টেলিভিশনে বাবরি মসজিদ ভাঙার দৃশ্য দেখানো বন্ধ করা হয়েছে। রাস্তায় বিরোধী দল আর সরকারি দলের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করতে গিয়েছেন। অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু তারপরও নিরাপত্তা নেই হিন্দুদের, তারপরও কোনও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বন্ধ হচ্ছে না।
মানববন্ধনে যোগ দেওয়ার সময় আমার নেই। আমার দিন কেটে যায় রোগীর চিকিৎসায়। ইমারজেন্সিতে ক্যাসুয়ালটির সংখ্যা কমছে না। খবর আসে পুরোনো ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে অতিরিক্ত ভিড় রোগীর, অনেককে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলে।
সে রাতে আমি অবকাশে ফোন করে জিজ্ঞেস করি প্রতিবেশিদের ওপর কোনও আক্রমণ হচ্ছে কি না। আমলাপাড়া এলাকাটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। আমাদের বাড়িটিই ছিল প্রথম একটি মুসলমানের বাড়ি, এরপর ধীরে ধীরে আরও কিছু মুসলমান এসে বসত শুরু করেছে, একাত্তর সালের আগে আরও হিন্দুর বাস ছিল, অনেকে ভারতে আশ্রয় নিতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি, সে সব বাড়িতে মুসলমান উঠেছে এখন। কিন্তু এখনও সংখ্যায় হিন্দুরাই বেশি এলাকাটিতে। মা আমাকে বলেন যে হিন্দুদের অনেকে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে অন্য কোথাও, অনেকে আছে, তবে তিনি কোনও আক্রমণের কথা শোনেননি। পাড়া থমথম করছে। কেউ বেরোচ্ছে না বাইরে তেমন। আমি মাকে বলি পাড়ার কেউ যদি আশ্রয় চায় অবকাশে, মা যেন কাউকে ফিরিয়ে না দেন। মা আরেকটি খবর আমাকে জানালেন যেটি আমাকে কষ্ট দেয় আবার স্বস্তিও দেয়, ছটকুর এক বন্ধু আছে ভুলন নামে, ছেলেটি ভয়াবহ ধরণের ছেলে, যে কাউকে খুন করতে দ্বিধা করে না রকমের ছেলে, ছেলেটি পৌরসভা থেকে কমিশনার পদে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে, তাই ভোটের আশায় সে হিন্দুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে, হিন্দুরা কথা দিয়েছে ভুলনকে ভোট দেবে, ভুলনের মত সন্ত্রাসীর ওপর আজ আমলাপাড়ার অসহায় লোকেরা নির্ভর করছে।
হঠাৎ নিজেকে আমার ডলি পালের মত, গায়ত্রী মন্ডলের মত, গৌতম বিশ্বাসের মত মনে হয়। নিজেকে আমার হিন্দু বলে মনে হতে থাকে। একটি ভয় শিরদাঁড়া বেড়ে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে। একটি ক্রোধ উঠে আসে আমার হাতের মুঠিদুটোয়, উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আমার। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে অস্থির হাঁটি। শেষে নির্মলেন্দু গুণের মত পা গুটিয়ে বসে থাকি বিছানায়। আমার মনে হতে থাকে আমি হিন্দু বলে আমাকে মেরে ফেলা হবে। পরদিন হাসপাতালে বসেই খবর পাই চট্টগ্রামে সাতশ বাড়ি ভস্মীভুত। খবর পাই ভোলার অবস্থার। ভোলার হিন্দু এলাকাগুলো এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দশ হাজার পরিবার গৃহহারা হয়ে খোলা আকাশের নিচে বসে আছে। ভোলার এমপি আওয়ামি লীগের তোফায়েল আহমেদ বসে আছেন ঢাকায়! কেন! তাঁর কি দায়িত্ব ছিল না তাঁর এলাকায় থাকা, আগে থেকেই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করা! আমার মনে হতে থাকে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সুবিধের জন্য আওয়ামি লীগও চাইছে হিন্দুর ওপর নির্যাতন হোক। এই ইস্যু নিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে চমৎকার মাঠে নামা যাবে। আমার রাগ হয় রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর। আমার ঘৃণা হয় নেতাদের কীর্তিকলাপে। ইচ্ছে করলেই ঠেকানো যেতে পারত এই সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস। ভারত সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে দাঙ্গা দমন করেছে অনেক। ভারতে দাঙ্গা হয়, ওখানে মুসলমানও হিন্দুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশে দাঙ্গা হয় না, হয় সন্ত্রাস। মুসলমানরা হিন্দুর ওপর নির্যাতন করে। হাসপাতালের ডিউটি সেরে বেরিয়ে পড়ি পুরোনো ঢাকার দিকে। জামাতে ইসলামির মিছিল ভারতীয় দূতাবাসের দিকে যাচ্ছে স্মারকলিপি দিতে। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্ররা মিছিলে স্লোগান দিচ্ছে ‘গোলাম আযম আদভানী ভাই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই।’ মৌলবাদীদের চরিত্র প্রতিটি দেশেই এক। এখন মৌলবাদী দুই নেতাকে ফাঁসি দিলেই সমস্যার সমাধান হবে কি! মন বলে, হবে না। হবে না কারণ নতুন নেতা গজাবে। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, পচা পুরোনো সমাজ ব্যবস্থা মৌলবাদ গজাতে চিরকালই সাহায্য করবে। মৌলবাদীরা যখন মাথা ফুঁড়ে বেরোয়, তখন কেবল দুএকটি শান্তিমিছিল আর সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্বের কথা চিৎকার করে বললে কাজ হয় না। তাই একদিকে মানববন্ধন হচ্ছে, অন্যদিকে মানবনির্যাতন চলছে। পুরোনো ঢাকার প্রতিটি অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখি। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে নিয়ে এসেছিলাম তারাপদ রায় আর তাঁর স্ত্রীকে, যখন কলকাতা থেকে ঢাকায় বেড়াতে এসে একদিন মন্দিরটি দেখতে চেয়েছিলেন — আজ সেই মন্দির ভাঙা, পোড়া, ধ্বংসস্তূপের পাশে কয়েকটি পুলিশ বসে আছে। পুলিশ যদি বসানোই হল, পুলিশ কেন ছয় তারিখ রাতেই বসানো হয়নি! আমার প্রশ্নের উত্তর কে দেবে! যতগুলো মন্দির আছে এলাকায় সব মন্দিরেই হামলা চলেছে, হিন্দুদের দোকান পাট একটিও অক্ষত নেই। বাড়িঘর ধ্বংস। তাঁতিবাজারে নেমে আমি হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে একটি সরু গলিতে ঢুকে দেখি একটি পোড়া বাড়ির স্তূপের ওপর বসে আছে এক লোক। উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে আছে পোড়া কাঠ, পোড়া বই, পোড়া কাপড়চোপড়। কাছে গিয়ে লোকটির নাম জিজ্ঞেস করলে লোকটি কোনও উত্তর দিল না। আমি কে, আমি কেন, ইত্যাদি কোনও কিছুতে তার কোনও আকর্ষণ নেই। পোড়া কাঠের মত বসে পোড়া ভিটের দিকে চেয়ে আছে লোকটি। সব হারাবার পর যে শূন্যতা থাকে, সে শূন্যতাও আর তার চোখে আর নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি ধ্বংসস্তূপের কাছে। গলি ছেড়ে এসে একটি লোক আমার দিকে উৎসুক তাকায়। তাকেই জিজ্ঞেস করি, ‘ওই যে লোকটি বসে আছে, ওর নাম কি জানেন?’
‘ও তো সতীপদ। সতীপদ দাস।’
আলো নিভে আসছে বিকেলের। হাঁটতে হাঁটতে গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠি। ইচ্ছে হয়েছিল সতীপদর কাঁধে একটি হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিই, বলি যে ‘মানববন্ধন হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিছিল হচ্ছে, মহল্লায় মহল্লায় শান্তি ব্রিগেড গড়ে তোলার কথা হচ্ছে। পত্রিকায় বুদ্ধিজীবীরা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে কড়া কড়া কলাম লিখছেন, বাংলাদেশ রুখে দাঁড়াবে ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, আপনি মোটেও দুশ্চিন্তা করবেন না, আর কেউ আপনার কোনও অনিষ্ট করবে না কোনওদিন,’ কিন্তু পারিনি বলতে। আমি অনুভব করি, একটি লজ্জা আমাকে গ্রাস করছে। আমার মুসলমান নামটি নিয়ে আমি লজ্জায় মাথা নুয়ে আছি। মানুষের ওপর মানুষের এই হিংস্রতা আমাকে লজ্জা দিচ্ছে। বিংশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে এসে, যখন সভ্যতা জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি আর একই সঙ্গে মানবতার অকল্পনীয় বিকাশে ব্যস্ত, তখন এক মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রচণ্ড নিষ্ঠুর বিবেকহীন জল্লাদের মত আরেক মানুষেরই ওপর, কারণ সেই মানুষ ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী। সে রাতে আমি এক ফোঁটা ঘুমোতে পারিনি। সারারাত জেগে থাকি আমি আর আমার দীর্ঘশ্বাস। ভোরের দিকে শুয়ে শুয়ে লিখি আমার লজ্জার কথা। সতীপদকে স্পর্শ করতে না পারার লজ্জা।
আমার লজ্জা যায় না। লজ্জা নিয়েই আমি আরও দুদিন নির্মলেন্দু গুণের বাড়িতে যাই, কেমন আছেন তিনি দেখতে যাই। দেখি ছেঁড়া কাঁথায় মুখ মাথা ঢেকে তিনি শুয়ে আছেন। মুখ ঢেকেছেন কেন জিজ্ঞেস করলে বললেন, ‘কিছু যেন দেখতে না হয়।’ নির্মলেন্দু গুণকে এ অবস্থায় দেখতে আমার ভাল লাগে না। তিনি সেই আগের মত শহরে ঘুরে বেড়াবেন। আজিমপুরে নিজের একটি ছাপাখানা না হলেও কম্পোজখানা দিয়েছেন, সেখানে বসে লিখবেন নিজের লেখা, অবসরে দাবা খেলবেন, বিকেলে ইত্যাদিতে বসে আড্ডা দেবেন, অনুষ্ঠানে কবিতাপাঠের আমন্ত্রণ পেলে কবিতা পড়ে আসবেন ঋজু দাঁড়িয়ে। যে কথা কখনও ভাবিনি নির্মলেন্দু গুণ উচ্চারণ করবেন, সে কথা শুনি তাঁর কণ্ঠে, মৃত্তিকাকে তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন। গুণকে বলি, ‘এসব কি ভাবছেন, মৃত্তিকা চলে গেলে আপনি এখানে একা থাকবেন কি করে?’
গুণের সঙ্গে নীরা লাহিড়ির বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের একটি মাত্র সন্তান মৃত্তিকা, যদিও সে তার দিদিমার বাড়িতে থাকে, গুণই দেখাশোনা করেন তার। তাঁর জীবন বলতে এই মৃত্তিকা—প্রচণ্ড ভালবাসেন মেয়েকে। মেয়েটিকে একদিন না দেখলে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। প্রতিদিন মেয়েকে ইশকুলে দিয়ে আসা, ইশকুল থেকে নিয়ে আসার কাজ তিনিই করেন। নীরা লাহিড়ি কুমিল্লায় চাকরি করেন, কালেভদ্রে মেয়েকে দেখতে আসেন। গুণ মেয়ের কাছাকাছি আছেন, আছেন মেয়ের প্রতিদিনকার প্রতিটি আবদার মেটাতে। এক বাড়িতে না থাকলেও পিতা কন্যার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। গুণ যে টাকা রোজগার করেন, তার সিংহভাগ খরচ করেন মৃত্তিকার জন্য, বাকিটা দিয়ে নিজেকে এবং গীতার পরিবারকে কায়ক্লেশে চালান। মৃত্তিকাকে স্নেহে আদরে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে বড় করে তোলাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। আর এখন তিনি ভাবছেন কলকাতা পাঠিয়ে দেবেন! আমি চমকে উঠি। বিস্ময় আমাকে অনেকক্ষণ নির্জীব করে রাখে।
‘না গুণ দা, মুত্তিকাকে কোথাও পাঠাবেন না। কেন পাঠাবেন? এটা আপনার দেশ, এই দেশ মৃত্তিকার। দেশ ছেড়ে ও যাবে কেন!’ শব্দগুলো একটি শোকার্ত হাওয়ায় ধাককা লেগে ক্ষীণ হয়ে আসে।
আমার লজ্জা যায় না। খবর পাই সিলেটে চৈতন্যদেবের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে মৌলবাদীরা। চারশ বছরের পুরোনো লাইব্রেরীটিও রোষ থেকে রক্ষা পায়নি। ইচ্ছে হয় চিৎকার করে কাঁদি। মানুষের মনুষ্যহীনতার জন্য নিজের মানুষ পরিচয়টিই আমাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে। আমার চেনা জানা অনেকে ভোলায় দুর্গতদের অবস্থা দেখে ফিরে বর্ণনা করেছে বীভৎস বর্বরতার কাহিনী, সহস্র নির্যাতিতের হাহাকার, ক্রন্দন। আমি ছটফট করি। যেন আমি নিজেই ভোলার খোলা মাঠে বসে থাকা একজন উদ্বাস্তু, জীবনের যা কিছু সহায় সম্পদ ছিল সব লুট হয়ে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, সর্বস্বান্ত একজন কেউ। এই অনুভবটি আমার থেকে যায় সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস কমে আসার পরও। হিন্দুদের দেশ ত্যাগ করার খবর শুনছি। কেউ কেউ বলে, ‘ওদের এটা উচিত হচ্ছে না, দেশে থেকে লড়াই করা উচিত ছিল।’ আমি নিজেকে একজন হিন্দুর জায়গায় বসিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি নিরাপত্তাহীনতার বোধ কতটা তীব্র হলে মানুষ দেশ ত্যাগের মত একটি ভয়ংকর সিদ্ধান্ত নেয় বা নিতে পারে। নিজেকে আমার মনে হতে থাকে আমি তাঁতিবাজারে বাস করা এক হিন্দু নামের যুবক, সুরঞ্জন দত্ত, আমি ধর্ম মানি না, আমি প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, আমার বন্ধুরা বেশির ভাগই ধর্মহীন, আমার দেশটিকে আমি ভীষণ ভালবাসি, দেশের মঙ্গলের জন্য দিন রাত ভাবি আমি, কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস আমাকে চূর্ণ করে দিচ্ছে, আমার আদর্শ ধ্বসে পড়ছে, দেশের জন্য আমার ভালবাসা আমার আবেগ সব নিবে যাচ্ছে, সকলের দিকে আমি সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছি, আমার ভয় হচ্ছে মুসলমানরা বুঝি এই আমাকে মারতে এল, সন্তা্রাস থেমে যায় কিন্তু আমার নিরাপত্তাহীনতা যায় না কোথাও, আমার ভয় হতে থাকে যে কোনও একদিন যে কোনও অজুহাতে আমার ওপর আক্রমণ হবে, শেষ পর্যন্ত, যদিও আমি চাই না, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করি, কিন্তু হেরে যাই, নিরাপত্তহীনতা আমাকে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। আমি চোখ বুজে ভাবছি দৃশ্য, তাঁতিবাজারের একটি দু ঘরের ছোট বাড়ি, বাবা মা বোন নিয়ে সংসার.. ভাবছি.. ভাবনা শেষ হয় না আমি কাগজ কলম নিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে লিখি, ‘সুরঞ্জন শুয়ে আছে। মায়া বারবার তাড়া দিচেছ, দাদা ওঠ, কিছু একটা ব্যবস্থা কর।’ সাত তারিখ থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত সুরঞ্জনের দিনগুলো আমার ভাবনার ঢেউএ উথালপাথাল করে। ঘরে বসে লেখার সময় আমার নেই। দৌড়োতে হয় হাসপাতালে। অপারেশন থিয়েটারে রোগীর শিরায় থাইয়োপেন্টাল সোডিয়াম আর সাকসামেথোনিয়াম ঢুকিয়ে, নাকে নাইট্রাস অক্সাইড আর অক্সিজেনের ঘ্রাণ দিয়ে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে রোগীর নাড়ি আর রক্তচাপ দেখে নিয়ে সার্জনকে ইঙ্গিত দিই অপারেশন শুরু করার। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। ওখানে রোগীর মাথার কাছে বসে রোগীর ফুসফুসে অক্সিজেন পাঠাতে হত যন্ত্রের বেলুন চেপে চেপে। এখানে হাতে কিছু চাপার দরকার হয় না, যন্ত্রই চেপে দেয়। আমার তাই জ্ঞানহীন রোগীর পাশে তেমন কিছু করার থাকে না, মাঝে মাঝে নাড়ি আর রক্তচাপ আর শ্বাসপ্রশ্বাসের ঘনত্ব দেখা ছাড়া আর দীর্ঘ অপারেশনের সময় উঠে উঠে শরীর অবশ করার ইনজেকশন দেওয়া ছাড়া। রোগীর কাছাকাছি বসে লিখে যেতে থাকি সুরঞ্জনের গল্প। সার্জন যখন বলেন অপারেশন শেষ, তখন উঠতে হয়, ইনজেকশন দিয়ে রোগীকে জাগাতে হয়। চোখ খোলা রোগীকে নামিয়ে নতুন রোগী টেবিলে তোলা হবে। কাগজ কলম আমার পকেটেই থাকে। অপারেশন চলাকালীন জ্ঞান হারানো আর জ্ঞান ফিরে পাওয়ার মাঝখানের সময়টুকু সুরঞ্জনের জন্য ব্যয় করতে থাকি।
পূরবী বসু আমাকে একদিন ফোনে বললেন, ‘সকলে কলাম লিখছে, তুমি এই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কিছু লিখছ না যে!’ বড় বিব্রত বোধ করি আমি। কোনও কলাম লেখা হয়নি আমার। বিপর্যস্ত মন নিয়ে কি লিখব কিছুই পারিনি ঠিক করতে, যে কথাই লিখতে চেয়েছি দেখেছি অন্যরা লিখে ফেলেছেন।
‘পূরবী দি, আমি কলাম লিখিনি, তবে বড় একটা কিছু লেখার চেষ্টা করছি। তথ্যভিত্তিক লেখা।’
তথ্য ভিত্তিক, কিন্তু তথ্য পাই কোথায়! পুরোনো ঢাকার অলিগলি ঘুরে একতা পত্রিকার আপিসে গিয়ে কোথায় কোন জায়গায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, তার সরেজমিনে তদন্তের তথ্যগুলো নিয়ে আসি। একতা কমিউনিস্ট পার্টির কাগজ, এতে বিস্তারিত খবর ছাপা হয়েছে দেশের কোথায় কি ঘটেছে। সংবাদ, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজও যথেষ্ট খবর ছেপেছে। এই হল আমার তথ্য সামগ্রী আর আছে নিজের চোখে দেখা ঢাকা এবং ঢাকার আশে পাশের এলাকায় ঘটা তাণ্ডব।
খুব অল্প কথায়, অল্প বর্ণনায় মূলত তথ্য দিয়ে হিন্দুদের অবস্থার বর্ণনা করে লেখা এটিকে না বলা যায় গল্প, না বলা যায় উপন্যাস। বইটির নাম দিই লজ্জা। ফেব্রুয়ারি মাস চলে আসছে, বই ছাপাতে ব্যস্ত বাংলাবাজারের সব প্রকাশক। পার্ল পাবলিকেশন্সের মালিক আলতাফ হোসেন মিনু অগ্রিম টাকা দিয়ে গেছেন। তিনি একটি বই পাবেনই ফেব্রুয়ারিতে নিশ্চিত। ভাল একটি রমারমা উপন্যাস পাওয়ার উত্তেজনায় লাফানো মিনুকে বড় দ্বিধায় বড় সংকোচে বড় লজ্জায় দিই লজ্জার পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে মিনুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করলেন, ‘এইটা কী দিলেন? উপন্যাস তো?’
‘না, ঠিক উপন্যাস না।’
‘তাইলে কি? গল্প সংকলন?’
‘না। তাও না।’
‘তাইলে কী এইটা?’
‘সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লেখা একটা বই।’
‘প্রবন্ধের বই?’
‘না, ঠিক প্রবন্ধও না।’
‘তাইলে কী এইটা।’
‘এইটা এমন কিছু না। খুব তাড়াতাড়ি কইরা একটা লেখা লিইখা ফেলছি। হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হইল ডিসেম্বরে, সেই সম্পর্কে।’
মিনুর উজ্জ্বল মুখটি মুহূর্তে কালো হয়ে যায়। তিনি মন খারাপ করে বললেন, ‘এই বই তো চলবে না।’
বড় সংকোচে বলি, ‘জানি বইটা চলবে না। কিন্তু এটা ছাপেন আপাতত, যেহেতু অন্য কোনও লেখা হাতে নাই। আমি কথা দিচ্ছি, আপনাকে আমি একটা উপন্যাস লিখে দেব।’
মিনু খুশি হয়ে ওঠেন উপন্যাসের কথায় এবং কথা দেওয়ায়।
লাল ঝরা জিভখানি নড়ে ওঠে, ‘কবে দিবেন?’
‘যত তাড়াতাড়ি পারি।’
‘বইমেলায় ধরতে পারবো?’
‘চেষ্টা করব।’
‘সত্যি কইতাছেন?’
‘সত্যি।’
লজ্জার পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে মিনু যখন যাচ্ছেন, তাঁর ব্যবসায় ক্ষতির কথা ভেবে আমার মায়া হয় খুব। বড় বিমর্ষ বিষণ্ন কণ্ঠ আমার, ‘এই বইটার ওপর আশা করবেন না। এই বই চলার মত না। বেশি ছাপানোর দরকার নাই। অল্প করে ছাপেন। আপনার যেন কোনও লস না হয়।’
মিনু আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ‘লস হইলে হোক, আপনে যহন লেইখ্যাই ফেলছেন, আমি ছাপবো। পরে আপনের একটা উপন্যাস ছাইপা এইটার লস পুষাইয়া নিব।’
১৯. নিষিদ্ধ গন্ধম
কলকাতা যেতে হবে। আবৃত্তিলোকের কবি সম্মেলনে কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ। সৌমিত্র মিত্র ঢাকায় চলে এসেছেন ঢাকার কয়েকজন কবিকে নিজমুখে আমন্ত্রণ জানাতে। আমার বাড়িতে বসেই ঠিক হল কাদের কাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। সৌমিত্র মিত্র নিজে কজন কবিকে আমন্ত্রণ পত্র দিয়েছেন, বাকিগুলো বিলি করার ভার আমার ওপর। আমার কানে কানে তিনি বলে যান, ‘এবারের অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ কিন্তু তুমি।’ মূল আকর্ষণের জন্য যত না, তার চেয়ে বেশি আনন্দ প্রিয় কলকাতাটি দেখার। উত্তেজনায় আমি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছি না কোথাও। কলকাতার অনুষ্ঠান শেষ হলে দার্জিলিং চলে যাব, শান্তিনিকেতন ঘুরে আসব, থাকব পুরো দু সপ্তাহ, এ হল গোপন ইচ্ছে। দু সপ্তাহের জন্য ক্যাজুয়াল লিভ নেওয়া যায় না। ডাক্তার রশীদ পরামর্শ দিলেন আর্ন লিভ নেওয়ার। আর্ন লিভের জন্য দরখাস্ত করে দিই।
নির্মলেন্দু গুণ দেশে নেই। কায়েস নামে গুণের এক ভক্ত গুণকে আমেরিকায় বেড়াতে নিয়ে গেছে। অসীম সাহা কোনও এক অজ্ঞাত কারণে প্রথমে রাজি হয়েও পরে আর রাজি হলেন না কলকাতায় যেতে। আমি শামসুর রাহমানএর বাড়ি থেকে তাঁর পাসপোর্ট আর ভিসার কাগজে তাঁর সই নিয়ে নিজেই দৌড়ে দৌড়ে ভিসা করিয়ে টিকিট করে আনি। নিজের ভিসা টিকিটও করি। টানা এক সপ্তাহ বেইলি রোডের দোকান থেকে প্রিয় প্রিয় মানুষের জন্য জামদানি শাড়ি আর আদ্দির পাঞ্জাবি কিনেছি, বইপাড়া থেকে কারও জন্য বই, শান্তিনগর বাজার খুঁজে কারও জন্য শুঁটকি মাছ, কারও জন্য মুক্তাগাছার মণ্ডা, নকশি কাঁথা, বড় ভালবেসে কারও জন্য বয়াম ভরে আমের আচার আর পুরো কলকাতার জন্য নিয়েছি থোকা থোকা ভালবাসা, সে অবশ্য কোনও সুটকেসে আঁটেনি। যাবার দিন কায়সারের গাড়িতে করে শামসুর রাহমানকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে বিমান বন্দরে গিয়েছি। যেন সৌমিত্র মিত্রর কোনও অনুষ্ঠান নয়, আবৃত্তিলোকের কোনও ব্যপার নয়, যেন অনুষ্ঠানটি আমার, যেখানে যাচ্ছি। যেন কলকাতা আমার শহর, যে শহরে সকল কবিকে আমি পরম পুলকে সাদরে সগৌরবে নিয়ে যাচ্ছি। আমার উচ্ছলত!ই সবচেয়ে বেশি। বিমান বন্দরে বেলাল চৌধুরী আর স্থপতি-কবি রবিউল হুসাইন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সুটকেসগুলো চেক ইন পার করে দিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে মহাআনন্দে এগোতে থাকি সামনে। মহানন্দেই পাসপোর্ট দিই ইমিগ্রেশনের লোকের হাতে। শামসুর রাহমান আর আমি সামনে, আমাদের পেছনে বাকি সব কবি। আমার তখন কখন দমদম পৌঁছবো, কখন চৌরঙ্গি, পার্ক স্ট্রিট, কলেজ স্টিট, গড়িয়াহাট, চিৎপুরে টই টই করে ঘুরে বেড়াব, কখন প্রিয় প্রিয় কবিদের সঙ্গে কলকাতায় জমিয়ে আড্ডা দেব, এই তাড়া। লোকটি আমার পাসপোর্ট থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকান। আবার পাসপোর্টে চোখ, আবার আমার মুখে। এরপর পকেট থেকে একটি ছোট কাগজ বের করে একবার কাগজে চোখ, আরেকবার পাসপোর্ট। লোকটি আমাকে পাসপোর্ট হাতে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যান ইমিগ্রেশনের কোনও বড় কর্তার ঘরের দিকে। বড় কর্তা আর লোকটি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে কিছু কথা বলেন। কি কথা বলেন কে জানে! আমার পাসপোর্ট নিয়ে কি কথা বলার থাকতে পারে! পাসপোর্টে যে ছবি, সে তো আমারই ছবি। পাসপোর্টে যে নাম ঠিকানা সে তো আমারই নাম ঠিকানা। তবে কিসের এত কানাকানি কথা! লোকটি ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি চাকরি করেন?
হ্যাঁ করি।
কোথায়?
ঢাকা মেডিকেলে।
বিদেশে যাওয়ার পারমিশান আছে আপনার?
বিদেশে যেতে আবার কারও পারমিশান লাগে নাকি!
লোকটি আমাকে বলেন না কার পারমিশান লাগে। কেবল বলেন, অনুমতি না থাকলে আপনার যাওয়া হবে না। আমরা বড় কর্তার ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি ঘটনা কি। ঘটনা কি তিনিও বুঝিয়ে বলেন না। বড় কর্তার সামনের তিনটে চেয়ারে আমরা বসি। আমি, শামসুর রাহমান, বেলাল চৌধুরী। পেছনে দাঁড়িয়ে রবিউল হুসাইন। দরজার বাইরে বাকি কবিরা। বড় কর্তার বোধহয় মায়া হয় আমাদের দেখে। কত চোর ছেঁচড় গুণ্ডা বদমাশকে পার করে দিচ্ছেন তিনি, অথচ যে মানুষ দল বেঁধে কবি সম্মেলনে যাচ্ছে, তাকে আটকাতে হচ্ছে। তিনি আমাদের দিকে একটি টেলিফোন এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ওপর থেকে কেউ ফোনে অর্ডার করলে আমরা ছেড়ে দেব।’ টেবিলে দুটো টেলিফোন ছিল। আরেকটি টেলিফোন ঘন ঘন বাজছে, বড় কর্তা রিসিভার কানে নিয়ে ঘন ঘনই বলছেন, ‘জি সার উনি এখানেই, জি স্যার আমার সামনেই বসে আছে, জি স্যার যেতে দেওয়া হচ্ছে না, জি স্যার ঠিক আছে।’ বড় কর্তা কি আমার কথা বলছেন ফোনের ওপারের স্যারকে! আমার সন্দেহ হয়, তিনি আমার কথাই বলছেন। ওই স্যারটি নিশ্চয়ই আগে থেকেই কোনও আদেশ দিয়ে রেখেছেন যেন আমাকে যেতে বাধা দেওয়া হয়।
এদিকে বেলাল চৌধুরী আর শামসুর রাহমান ওপরের মানুষগুলোকে এক এক করে খুঁজছেন মরিয়া হয়ে। সে যে কী শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। বেলাল চৌধুরী বললেন, ‘হেলথ সেক্রেটারি আমাদের বন্ধু, তাঁকে একবার পাওয়া গেলে কোনও সমস্যা নেই।’ বার বার ফোন করেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। বেলাল চৌধুরী আইজির নম্বরে ফোন করেন, আইজি নেই। শামসুর রাহমান তাঁর এক মন্ত্রী বন্ধুকে ফোন করেন, তিনি ঢাকার বাইরে। সময় দ্রুত এগোচ্ছে। উড়োজাহাজে উঠে গেছে সব যাত্রী। কবির দলটি কেবল বাকি। মনকে বলছি, স্থির হও, দুর্যোগ কেটে যাবে। কিন্তু মন কিছুতে স্থির হচ্ছে না। সময় যাচ্ছে, নির্দয় সময় সামান্য করুণা করছে না আমাদের। টেলিফোনে আঙুলের অনবরত সঞ্চালনের পর শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল কবি ইমরান নূরকে। তিনিই স্বাস্থ্য সচিব। ওপরের লোক। স্বস্তির একটি শ্বাস ফেলি আমরা। আমাদের ঠোঁট থেকে উড়ে যাওয়া হাসিটি চকিতে ফিরে আসে। শামসুর রাহমান বললেন, ‘আমরা কলকাতা যাচ্ছি, কিন্তু তসলিমাকে যেতে দিচ্ছে না, আপনি এদের বলে দিন যেন ওকে যেতে দেয়। আপনি বলে দিলেই হবে।’
ইমরান নূর কথা বলতে চাইলেন বড় কর্তার সঙ্গে। সাংকেতিক কথা কি না জানি না, আমাদের কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না কি কথা তাঁরা বলেন। বড় কর্তা কথা শেষ করে শামসুর রাহমানকে দিলেন রিসিভার। ইমরান নূর জানিয়ে দিলেন, ‘তসলিমার যাওয়া হচ্ছে না।’
‘কেন যাওয়া হচ্ছে না?’
‘দেশের বাইরে যেতে গেলে পারমিশান লাগবে সরকারের।’
‘সেটা আপনি ব্যবস্থা করে দিন। আপনি এখন এদের বলে দিলে কি হয় না?’
‘না হয় না।’
‘কিছুতেই কি হবে না? দেখুন একটু চেষ্টা করে হয় কি না।’
‘হয় না।’
শামসুর রাহমানের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বেলাল চৌধুরী মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন। আমার সামনে দুলে উঠলো ইমিগ্রেশন অফিসারের ঘরটি, ঘরের দেয়াল, দুলে উঠলো পুরো বিমান বন্দর, দুলে উঠল স্বপ্ন সুখ। আমাকে আর সামনে পা বাড়াতে দেওয়া হয় না। উড়োজাহাজ তখন ছাড়ছে ছাড়ছে প্রায়। ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে বাকি যাত্রীরা এখনই যেন জাহাজে উঠে যান। বেলাল চৌধুরী বিষণ্ন মুখে বললেন, ‘আমি থেকে যাই, আমি আর তসলিমা পরে আসছি। শামসুর রাহমান বললেন, না আপনি যান, আমি থেকে যাই, ঝামেলা মিটিয়ে আজ বিকেলের ফ্লাইটে না হয় আমরা যাবো।’ ওঁদের কথায় আমার চোখে জল চলে আসে। আমি বাস্পরূদ্ধ কণ্ঠে বলি, ‘আমার জন্য দেরি করবেন কেন? আপনারা চলে যান। আমি আসছি পরে।’
অধৈর্য হয়ে উঠছে বাকি কবিরা। কবিদের কারও কারও বিষণ্ন মুখ, কারও বা প্রসন্ন মুখ। সরকারি চাকরি করা আর কোনও কবিকে এই হাঙ্গামা পোহাতে হচ্ছে না। কারও জন্য সরকারি অনুমতির প্রয়োজন হয়নি। কেবল আমার জন্য প্রয়োজন। দলের মধ্য থেকে রফিক আজাদ শামসুর রাহমানের হাত ধরে ‘আসুন তো, প্লেন ছেড়ে দিচ্ছেঞ্চ বলে টেনে নিয়ে যান সামনে। বেলাল চৌধুরী বলে গেলেন, ‘এক্ষুনি তুমি ইমরান নূরের অফিসে চলে যাও, দেখ কি করতে বলে, করে, আজ বিকেলের ফ্লাইটেই চলে এসো। আজ যদি সম্ভব না হয়, তবে কাল সকালের ফ্লাইটে যে করেই হোক এসো।’
আমাকে পেছনে রেখে দলের সবাই উড়োজাহাজের দিকে এগোতে লাগলেন। শামসুর রাহমান বার বার করুণ চোখে তাকাচ্ছিলেন পেছনে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকা আমার দিকে। আমি একা দাঁড়িয়ে। দলের শেষ মানুষটি যখন অদৃশ্য হয়ে যায়, এক বন্দর মানুষের সামনে আমি হু হু করে কেঁদে উঠি। ওঁদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আমার যে এমন ঝড় বইবে বুকে, এমন যে উথলে উঠবে কষ্ট, তা আমি তখন বুঝিনি। কাচের ঘরের মত ভেঙে গেল আমার স্বপ্নের দালানকোঠা। পুরো বন্দর শুনল সেই ভাঙনের শব্দ, পুরো বন্দর শুনল আমার বুক ছেঁড়া আর্তনাদ।
আমাকে পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হল না। হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলা হল, ‘এই কাগজটি দেখিয়ে এসবি অফিস থেকে আপনার পাসপোর্ট নিয়ে নেবেন।’
‘কখন দেবে পাসপোর্ট?’
‘আজকে বিকালে গেলে বিকালেই পাবেন। যদি না হয়, কালকে সকালে তো পাবেনই।’ উড়োজাহাজের পেটের ভেতর থেকে ফেরত এসেছে নম্বর সাঁটা আমার দুটো সুটকেস। সুটকেসদুটো সামনে নিয়ে অনেকক্ষণ অবশ বসে থাকি। হঠাৎ কি করে কি হয়ে গেল, পুরোটাই যেন আস্ত একটি দুঃস্বপ্ন। এখনও আমার ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না সত্যি সত্যিই ঘটে গেছে এমন মর্মান্তিক একটি ব্যপার।
কায়সার প্রায় সকালে বিজয়নগরে তার এক বন্ধুর আপিসে গিয়ে বসে। সেখানে ফোন করে কায়সারকে পেয়ে তাকে বিমান বন্দরে আসতে বলি। কায়সার এলে বাড়িতে না গিয়ে সোজা সচিবালয়ে যাই ইমরান নূরের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাকে আলাদা ঘরে নিয়ে মুখোমুখি বসে বললেন তাঁর কোনও ক্ষমতাই নেই আমার জন্য কিছু করার। কেন তাঁর ক্ষমতা নেই তা তিনি বলতে চাইলেন না। বহির্বাংলাদেশ ছুটির জন্য আবেদন করার উপদেশ দিলেন কলকাতা যেতে হলে আমার বর্হিবাংলাদেশ ছুটি চাই। এরকম যে একটি ছুটি নেবার নিয়ম আছে তা আমার জানা ছিল না। হরদম দেখছি ডাক্তাররা দেশের বাইরে যাচ্ছেন, কাউকে এরকম ছুটি নিতে হয়নি। আমার বেলায় আইনের সাত রকম মারপ্যাঁচ। আইন মানতে আমার তো কোনও অসুবিধে নেই। সচিবালয় থেকে ছুটে যাই হাসপাতালে। দরখাস্ত লিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অগ্রায়ন নিয়ে সোজা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে দরখাস্তটি দেওয়ার পর তিনি দেখলেন, পড়লেন, বললেন আমি যেন কাল আসি। কাল কেন? আজই সই দিয়ে দিন। না, আজ সই হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? এটি আমার আজই দরকার। আজই দরকার হোক, কিন্তু হচ্ছে না।
বাড়ি ফিরে আসি। সৌমিত্র মিত্র ফোন করছেন বিকেলের ফ্লাইটে আসা হচ্ছে কি না আমার জানতে। বলে দিই হচ্ছে না।
‘কাল হবে?’
‘চেষ্টা করবো।’
পরদিন সকালে মালিবাগের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে পাসপোর্ট আনতে যাই। পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হয় না আমকে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বহির্বাংলাদেশ ছুটির কি হল দেখতে যাই, কিছুই হয়নি জেনে আবার ক্লান্ত বিপর্যস্ত আশাহত আমি ফিরে আসি। কলকাতা থেকে সৌমিত্র মিত্র বার বারই ফোন করে জানতে চাইছেন কতদূর এগিয়েছে যাওয়ার ব্যপারটি। বলছেন আমার জন্য সবাই ওখানে অপেক্ষা করছেন, আমি না গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। কেলেঙ্কারি হবে তো আমি কি করব, আমাকে তো পাসপোর্টই ফেরত দেওয়া হচ্ছে না। তার পরদিনও দেখি, তার পরদিনও। আমাকে কিছুই দেওয়া হয়না। না পাসপোর্ট। না ছুটি।
আমার কলকাতা যাওয়া হয় না।
কবিরা ফিরে এলে জিজ্ঞেস করি, কেমন হল সম্মেলন, কারা কারা কবিতা পড়ল, কেমন আছে কলকাতা, নন্দনে কী চলছে, রবীন্দ্রসদনে কী হচ্ছে, শিশির মঞ্চেই বা কী.. । ওঁরা বলেন, যতটুকু বলেন, শুনে আমার সাধ মেটে না।
বইমেলা এসে যায়। এর আগের বছরের মেলায় তসলিমা নাসরিন পেষণ কমিটির মিছিল বেরিয়েছে, মেলায় আমার বই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মেলা কর্তৃপক্ষ আমাকে মেলায় যেতে নিষেধ করেছেন। এ বছরের মেলায় অন্য সব কবি লেখকরা যাচ্ছেন, আমিই কেবল বসে আছি ঘরে। ঘরে মন বসে না। মন খেলায় মেতে ভেলায় ভেসে মেলায় যায়। একদিন আমার দুর্দমনীয় ইচ্ছে আমাকে খাঁচা ভেঙে বের করে আনে, যে করেই হোক যাবই আমি মেলায়। কিসের ভয় আমার! আমি তো কোনও অপরাধ করিনি। যে কোনও মানুষেরই অধিকার আছে মেলায় যাওয়ার। আমার কেন থাকবে না! আমি কেন নিজের ন্যূনতম স্বাধীনতাটুকু কর্তৃপক্ষের অন্যায় আদেশে বিসর্জন দেব! মেলায় যাওয়ার সিদ্ধান্তটি খসরুকে জানালে তিনি তাঁর দুজন বন্ধু সঙ্গে নেবেন বললেন। একা যাওয়ার তো প্রশ্ন ওঠে না, যেতে হবে সদলবলে। টাক-মাথা ছিপছিপে চশমা চোখের দার্শনিক চেহারার শহিদুল হক খান আমার নিরাপত্তা রক্ষক হিসেবে এগিয়ে এলেন। শহিদুল হক খান টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করেন, প্রচুর কথা বলেন কিন্তু সুন্দর কথা বলেন। তাঁর অনুষ্ঠানে আমাকে একবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম কিন্তু তাঁর দেওয়া নাট্যসভা পুরস্কারটি গ্রহণ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে একরকম বন্ধুতা গড়ে ওঠে আমার। আমার বাড়িতে দেখা হতে হতে খসরু আর শহিদুলের মধ্যেও জমে ওঠে। খসরু দেখতে যেমনই হোক, খুব হৃদয়বান মানুষ তিনি। বন্ধুদের জন্য যতটুকু করা উচিত তার চেয়েও বেশি করেন। ইত্তেফাকের সাংবাদিক আলমগীরের সঙ্গে পরিচয় হল আমার বাড়িতে, কদিন পরই তিনি আলমগীরকে তাঁর ব্যবসার অংশীদার করে নিলেন। আমার কখনও গাড়ি প্রয়োজন হলে তিনি নিজে যদি ব্যস্ত থাকেন, তাঁর গাড়িটি পাঠিয়ে দেন। হঠাৎ একদিন আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন আমার জন্য আস্ত একটি নতুন কমপিউটার নিয়ে এসে। খসরু ধনী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু দেশের আর ধনীদের মত তাঁর আচরণ নয়। কত মুক্তিযোদ্ধাকেই দেখেছি নিজের আখের গুছিয়ে নিয়ে আরাম করছেন, দেশকে শকুনে ঠোকরাচ্ছে কি শেয়ালে খাচ্ছে এ নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা করেন না। খসরু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তাঁর আদর্শ তিনি কারও কাছে বিক্রি করেননি। মুক্তিযদ্ধের পক্ষের শক্তিকে তিনি সাধ্যাতীত সাহায্য করেন। আওয়ামি লীগের নেতারা তাঁর কাছে গিয়ে বসে থাকেন দলের চাঁদার জন্য, কাউকে তিনি ফিরিয়ে দেন না। আমার একদিকে খসরু, আরেকদিকে শহিদুল হক, আমি হেঁটে যাই বইমেলার দিকে। আনন্দ আর আশঙ্কা দুটোই আমাকে কাঁপায়। মেলায় হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি চলবে না। কোনও একটি স্টলে কিছুক্ষণ বসে মেলার স্বাদ নিয়ে সাধ মিটিয়ে দু পাশে নিরাপত্তা নিয়ে ফিরে যেতে হবে, এই হল শুভাকাঙ্খীদের সিদ্ধান্ত। পার্ল পাবলিকেশন্সের স্টলে ঢুকতেই মিনু আমাকে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়েন। প্রচুর লোক নাকি আমার বই কিনছে, আমার অটোগ্রাফের জন্য বার বার ঘুরে যাচ্ছে। মেলার এই আলোকিত প্রাঙ্গন, লেখক পাঠকের এই মিলনকেন্দ্রটির উৎসব উৎসব পরিবেশ দেখে, গানের সুরে, কবিতার শব্দে কোলাহলে কলরোলে মুখরিত বইমেলাটি দেখে মুহূর্তের মধ্যে আমি ভুলে যাই আমার কোনও বিপদ আছে এখানে, যেন আর সব লেখকের মত বইমেলায় থাকার, ঘূরে বেড়াবার সব অধিকার আমার আছে। পুরো দেশটির সবচেয়ে সভ্য, শিক্ষিত, সবচেয়ে সচ্চরিত্র, সৎ সদাচারী, সুজন সজ্জন, স্বাধীনচেতা সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক মানুষেরা যে জায়গাটিতে জড়ো হন, নিরাপত্তা যদি সেখানে না থাকে তবে আর আছে কোথায়! আমার জন্য মসজিদ নিরাপদ নয়, কোনও রক্ষণশীল লোকদের আঙিনা নিরাপদ নয়, কোনও অন্ধকার গলি, কোনও নির্জন পথ নিরাপদ নয়, কোনও সন্ত্রাসীর আড্ডাখানা, মাতালের আস্তানা নিরাপদ নয়, কোনও ধর্মীয় জলসা নয়, কোনও জামাত শিবিরের আখড়া নয়, খল পুরুষের এলাকা নয়। নিজের ঘরের বাইরে যদি কোনও নিরাপদ কিছু আমার জন্য থেকে থাকে, তবে তো এই মেলাই। বড় চেনা এই মেলা আমার, বড় অন্তরে এই মেলা আমার,হৃদয়ের রক্তস্রোতে এই মেলা, প্রতিটি হৃদস্পন্দনে মেলা, এই মেলা আমার দীর্ঘ শোকের পরের অমল আনন্দ, সারা বছরের প্রাণপাত পরিশ্রমের পর এই মেলা যেন হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আবেশে চোখ বোজার প্রশান্তি। মিনু জানান, লজ্জা খুব বিক্রি হচ্ছে, কয়েকদিনেই প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে গেছে, এখন দ্বিতীয় মুদ্রণ চলছে, তিনি নিশ্চিত তাঁকে অচিরে তৃতীয় মুদ্রণে যেতে হবে। এ কদিনেই কয়েক হাজার লজ্জা শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটে না আমার। লজ্জা কেন লোকে কিনবে! লজ্জায় কী আছে! এটি কোনও প্রেমের উপন্যাস নয়, চমকপ্রদ কোনও কাহিনী নেই এতে, যে কথা সকলে জানে, সে কথাই গল্প আকারে লেখা, তথ্য ভারাক্রান্ত। পাঠক সাধারণত এসব বই পছন্দ করে না। পার্ল পাবলিকেশন্সের স্টলে বসার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ লাইন ধরে বই কিনতে শুরু করে। সবাই যে লজ্জার জন্য লজ্জা কেনে তা নয়। নতুন বই কেনার আগ্রহে কেনে। স্টলে এসে জিজ্ঞেস করে, তসলিমা নাসরিনের নতুন বই কী বেরিয়েছে? নতুন বই লজ্জা। একটা লজ্জা দিন। দু টা লজ্জা দিন। তিনটে লজ্জা দিন। অন্যান্য স্টলের লোক আসে নিতে, পঞ্চাশটা লজ্জা দিন, একশটা লজ্জা দিন। প্রথম ভেবেছিলাম সম্ভবত হিন্দুরা বইটি কিনছে। কিন্তু অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় অনেকেই তাদের নাম লিখতে বলে, নামগুলো হিন্দু নাম নয়। লজ্জা বিক্রি হয় আর আমার মনে ভয় জন্মাতে থাকে, যারা এই বই কিনছে, দু পাতা পড়ার পরই নিশ্চয়ই তাদের আর ভাল লাগবে না। তসলিমার লেখার ভক্ত বলে বইটি কিনছে, নাকি বিশেষ করেই লজ্জা কিনছে, জেনেই কিনছে কী আছে এতে, আমার বোঝা হয় না। সুযোগও হয় না ক্রেতাদের কাউকে জিজ্ঞেস করার। লজ্জার জন্য ভিড় বাড়তে থাকে। অটোগ্রাফের জন্য ভিড়। এক মুহূর্তের জন্য কলমকে অবসর দিতে পারি না। শহিদুল বসে আছেন পাশে। খসরু দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়, তাঁর বলশালী বন্ধুরা আশে পাশে কোথাও আছে। এত লোক আমাকে ভালবাসে, আমার বই পড়ে, আমার কেন নিরাপত্তার অভাব হবে এই মেলায়! তা সম্ভবত খসরুও অনুমান করেন, তিনি একটু ঘুরে আসি বলে জনারণ্যে হাওয়া খেতে যান। এর খানিক বাদেই ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি প্রথম আঁচ করতে পারিনি কেউই। স্টলের সামনের খোলা অংশটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। স্টলের বসে থাকা দাঁড়িয়ে থাকা সবাই লক্ষ করছি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘিরে থাকা মানুষগুলোর পেছনে শ তিনেক মানুষ দাঁড়িয়ে গেল। স্টল ঘিরে প্রচণ্ড ভিড়, কিন্তু কেউ বই কিনতে চাইছে না, কেউ সরছেও না। ভিড়ের লোকগুলো কি চায়, কেন এখানে খামোকা দাঁড়িয়ে আছে, কেন জায়গা দিচ্ছে না যারা বই কিনতে আসছে তাদের, তা স্টলের একজন চেঁচিয়ে জানতে চায়। তার জানতে চাওয়ার কোনও উত্তর মেলে না, কেবল একটি হৈ হৈ শব্দ ছাড়া। হৈ হৈ কিছুক্ষণ চলল। শব্দটি কোনও শোভন শব্দ নয়। মিনু আমাকে আস্তে করে আমার চেয়ারটি পিছিয়ে নিতে বললেন। ভিড় আর আমাদের মধ্যে মাত্র দেড় হাত দূরত্ব, দেড়হাতের মধ্যে লম্বা টেবিলের মত পাতা। আমি চেয়ার পিছিয়ে নিয়ে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে উদ্ভট সব শব্দ করা শুরু করল ভিড়ের লোকেরা। উদ্ভট শব্দ রূপান্তরিত হয় ‘ধর এরে মার এরেঞ্চশব্দে। ‘মাথা ফাটাইয়া দে, কাপড় খুইল্যা নে, হাত ভাইঙ্গা ফেলঞ্চশব্দে। স্টলের একজন ‘পুলিশ, পুলিশ কোথায়ঞ্চ বলে চেঁচাচ্ছে, মিনু তাকে দৌড়ে পুলিশ ডেকে আনতে বলেন। পুলিশ ডাকতে যাওয়ার পথ নেই কোনও। স্টল থেকে বেরোবার জন্য সূতো পরিমাণ জায়গা নেই। হঠাৎ ঢিল। একটির পর একটি ঢিল এসে পড়ছে আমার গায়ে। কানের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, ঘাড়ে পড়ছে, বুকে এসে লাগছে, হাতে লাগছে। আমাকে আড়াল করে ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছেন শহিদুল আর মিনু। আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক আর বিবর্ণ হয়ে আছি। বড় বড় ঢিল ছোঁড়া হচ্ছে স্টলের বইয়ের তাকে, বই হুড়মুড় করে পড়ছে নিচে, পাথর পড়ল বাল্বের ওপর, বাল্বের কাচ ছিঁটকে পড়ল আমাদের গায়ে। অন্ধকার হয়ে গেল পুরো স্টল। অনুচ্চ স্বরে স্টলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে দ্রুত কিছু বলে নিল। কুলকুল করে ঘামছে এক একজন। এরপর তিনশ লোকের ধাককা স্টলের দিকে। ধাককার চোটে সামনের যে টেবিলের বাধাটি ছিল সেটি ভেঙে পড়ল। পুলিশ থামের মত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এ পা ও এগোচ্ছে না। পুলিশের জন্য অপেক্ষা করার আর সময় নেই। আমার দিকে ধেয়ে আসা লোকেরা যে কোনও মুহূর্তে আমাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। আমাকে প্রাণে বাঁচাতে গেলে এই মুহূর্তে কিছু একটা করতেই হবে স্টলের লোকদের। মুহুর্তের মধ্যে যে যা পারেন, মেঝেয় মোটা মোটা কাঠ ছিল, বাঁশ ছিল, স্টল বানিয়ে বাড়তি জিনিসগুলো স্টলের ভেতরেই ছিল, সেগুলো দুহাতে তুলে নিয়ে একযোগে ভাঙা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে ধর ধর বলে ধাওয়া দিল। এক ধাওয়ায় ভিড় পিছিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটো পুলিশ দৌড়ে এসে আমার চিলের মত ছোঁ মেরে স্টল থেকে বের করে নিল, দুদিকে দুটো পুলিশ আমার দু বাহু শক্ত করে ধরে দৌড়োতে লাগল। পেছন থেকে আরও কিছু পুলিশ আমাকে সামনের দিকে ধাককা দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। আমার হাতব্যাগ কোথাও পড়ে গেছে, পায়ের জুতোও কোথাও খুলে গেছে, শাড়ি ঝুলছে খুলে, ওই অবস্থাতেই দৌড়ে আমাকে নিয়ে তুলল একাডেমির দোতলায়। আমাকে ভেতরে ঢুকিয়েই পুলিশ বন্ধ করে দিল লোহার দরজাটি। স্টল থেকে একাডেমির মূল দালানটিতে আসার পথের দু পাশে পুরো মেলার লোক ভিড় করে দেখছিল দৃশ্য। দৃশ্যটি নিশ্চয়ই দেখার মত ছিল। দোতলায় তখন আমার গা থরথর করে কাঁপছে। পুলিশেরা কথা বলছেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের সঙ্গে। মহাপরিচালক আমাকে ডেকে নিয়ে কড়া স্বরে বলে দিলেন, আমি যেন আর কখনও ভুলেও বইমেলায় না আসি। বাংলা একাডেমির বইমেলায় সারাজীবনের জন্য আমি নিষিদ্ধ।
যেরকম কালো গাড়ি করে চোর গুণ্ডাদের পাকড়াও করে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়, সেরকম গাড়িতে তুলে পুলিশেরা আমাকে শান্তিবাগের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল। পথে একজন পুলিশ বলল, ‘ধর্ম নিয়ে লেখেন কেন? ধর্ম নিয়ে লিখলে এইরকম কাণ্ড তো হবেই।’ আরেকজন বললেন, ‘আমরা না বাঁচালে আপনাকে আর বেঁচে ফিরতে হত না আজকে।’
খানিক পর শান্তিবাগে খসরু এলেন। শহিদুল হক খান এলেন। মিনু এলেন। সকলেই ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত। সকলে ফ্রিজ থেকে নিয়ে ঠাণ্ডা পানি খেলেন। মিনু জানালেন তাঁর স্টল পুরো ভেঙে ফেলেছে। বই সব লুট হয়ে গেছে। শহিদুল হক পায়চারি করতে করতে বললেন যে তিনি দেখেছেন হুমায়ুন আজাদ এবং আরও কিছু লেখক দূরে দাঁড়িয়ে ওইসময় চা খাচ্ছিলেন আর কাণ্ড দেখছিলেন। খসরু বললেন যে তিনি ভিড়ের জন্য নিজে তিনি স্টলের দিতে যেতে পারছিলেন না। পুলিশদের তাগাদা দিচ্ছিলেন কিছু একটা ব্যবস্থা করতে কিন্তু তারা মোটেও নড়তে চাইছিল না।
আমি স্তব্ধ বসেছিলাম। চোখের সামনে বারবারই ভয়ংকর দৃশ্যগুলো ভেসে উঠছে আর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে শরীর। স্টল থেকে ওই হঠাৎ ধাওয়াটি না দিলে কী হত অবস্থা, জিজ্ঞেস করি। কারও মুখে কোনও উত্তর নেই। কী হত, তা তাঁরাও নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেন।
একুশে ফেব্রুয়ারির আগের রাতে শহীদ মিনার লাল সূর্য আঁকা একটি কাপড় দিয়ে সাজানো হয়। আমার ওপর আক্রমণ হওয়ার ঘণ্টাখানিক আগে মিনারের লাল সূর্যটি পুড়িয়ে দিয়েছে কারা যেন! শহীদ মিনারের সূর্য পুড়িয়ে দেওয়া লোকগুলোই কি ভিড় করেছিল বইমেলার স্টলে, আলো নিভিয়ে দিয়েছিল স্টলের! অন্ধকার করে দিয়েছিল আমার স্বাধীনতার জগতটি!
২০. লজ্জাহীনতা
তসলিমা নাসরিনের লজ্জা উপন্যাস বাজেয়াপ্ত
গতকাল শনিবার এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, জনমনে বিভ্রান্তি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অঙ্গনে বিঘ্ন ঘটানো এবং রাষ্ট্রবিরোধী উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় তসলিমা নাসরিন রচিত লজ্জা (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ৯৩ পার্ল পাবলিকেশন্স, ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ হতে প্রকাশিত) বইটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯- ক (৯৯-অ) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং এর সকল কপি বিক্রয়, বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ১১ই জুলাই, ১৯৯৩
রবিবারের পত্রিকায় প্রথম পাতায় খবরটি ছাপা হয়। খবরটি আমাকে বিস্মিত করে, আমাকে চমকিত করে, আমাকে স্থবির করে আবার চঞ্চলও করে। লজ্জা বইটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিঘ্ন ঘটিয়েছে, এরকম অপবাদ কখনও কোথাও শুনিনি। বইটির গদ্য ভাল নয়, বইটি উপন্যাস হয়নি, তথ্যে ঠাসা বইটি বার বারই মনোযোগ নষ্ট করে, এসব শুনেছি। মানিও। বইটিতে ত্রুটি আছে, অবশ্যই। খুব অল্প সময়ের মধ্যে লেখা। প্রকাশকের চাপে বইয়ের গুণগত মানগত ব্যপারগুলো নিয়ে ভাবার জন্য মোটেও সময় পাইনি। কিন্তু যত দোষই দাও, বইটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিঘ্ন ঘটাবে এই দোষ তুমি দিতে পারো না মাননীয় সরকার। দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব বলেই বইটি লেখা, যেন সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়, যেন কোনও মানুষের ওপর তার ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের কারণে কোনও রকম নির্যাতন না হয়। শরীরে একটি মস্ত ঘা হয়েছে, এই ঘাটি খুলে দেখানোর উদ্দেশ্য একটিই, যেন চিকিৎসা পাওয়া যায়। এর মানে কি এই যে ঘাএর কথা বলে আমি শরীরের অপমান করেছি! যদি আমার নির্বাচিত কলাম আজ বাজেয়াপ্ত করা হত, আমি এত অবাক হতাম না। যদি নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্যকে নিষিদ্ধ করা হত, অবাক হতাম না। কারণ এই বইগুলোয় আমি ধর্ম সম্পর্কে আমার নিজস্ব মত ব্যক্ত করেছি, যে মত এ দেশের বেশির ভাগ লোকেরই সয় না। লজ্জায় আমি ধর্ম নিয়ে কোনওরকম মন্তব্য করিনি। বরং সব ধর্মের মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের অধিকার আছে, এবং তা থাকা উচিত, সে কথাই বলেছি। হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছে, কোথায় কী করে নির্যাতিত হচ্ছে, কেন তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, কেন তারা নিজের দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে অন্য দেশে, তাদের কষ্টের কথা, তাদের গভীর গোপন যন্ত্রণার কথা তাদের হয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করেছি।
লজ্জা বাজেয়াপ্ত হওয়ার কদিন পর একটি দীর্ঘ চিঠি আমার হাতে আসে। চিঠির শুরুতে লেখা গোপনীয়। চিঠিটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে পাঠানো, পাঠানো হয়েছে ঢাকা সেনানিবাস থেকে। সেনাবাহিনীর মহাপরিচালকের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার এম.এ.হালিম চিঠিটি লিখেছেন। সেনাবাহিনীতে, শুনেছি, দুটো দল আছে। এক দল ধর্মীয় চরমপন্থী, আরেক দল নরমপন্থী। চরমপন্থীরাই এই আদেশটি পাঠিয়েছে সরকারের কাছে। লিখিত ভাষাটিকে আদেশ বলে মনে না হলেও এটি আদেশ। সেনাবাহিনীর সীমাহীন ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সেনাবাহিনীর নিতম্বই এই স্বাধীন বাংলাদেশের গদি সবচেয়ে বেশিকাল স্পর্শ করেছে। অ-সেনা কিছু সরকারের মাথার পেছনে বন্দুকের নল ছিল, সে কথাও আমরা জানি। সেনাবাহিনী জানে, যে কোনও সময় তারা বন্দুক হাতে নিয়ে চলে আসতে পারে দেশ শাসন এবং শোত্র করতে। যে প্রধানমন্ত্রী এখন মহাসমারোহে ক্ষমতায় বসেছেন, তাঁর গাড়ির বহরও সেনানিবাস থেকেই যাত্রা করে। তিনি সেনা-স্ত্রী। সেনা থেকে নিস্তার নেই জনগণের। আমার থাকবে কেন! সেনাবাহিনী থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে লজ্জা নিষিদ্ধ করার, সুতরাং লজ্জাকে নিষিদ্ধ হতেই হবে। বন্দুকের সামনে মাথা নুয়ে আছে দেশের যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্তনেলেওয়ালাগণ।
চিঠিটির শুরুতে লজ্জার গল্পটি সংক্ষেপে বর্ণনা করে এবং লজ্জা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে শেষদিকে, শেষপৃষ্ঠায় লেখা, ‘এতদাঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সবচেয়ে অটুট। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলে দুএকটি বিচ্ছিত ঘটনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবার ঘটনা এই নয় যে, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নেই। সংখ্যালঘু হিন্দুরা চাকুরিতে সর্বক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে এবং কতক ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্যে হিন্দুদের অবস্থান সুসংহত। কিন্তু জনাবা তসলিমা নাসরিন বইটিতে হিন্দু নির্যাতনের কাল্পনিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। চাকুরি সংক্রান্ত ব্যপারে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। বইটির মাধ্যমে লেখিকা হিন্দুদের দারুণভাবে উসকে দিয়েছেন। আর একজন মুসলমান লেখিকার এহেন লেখা থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বাংলাদেশে হিন্দুদের নাগরিক অধিকার হরণ ও তাদের উপর নির্যাতনের অলীক ধারণাকে সত্য বলে ধরে নেবে। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে সহাবস্থানের মনোভাব ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
কারও লিখিত বই দ্বারা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টির অবকাশ থাকলে সে সকল বই বাজারে প্রকাশিত হতে না দেয়াই শ্রেয়। জনাবা তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে কটাক্ষ করে লজ্জা বইটি লিখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টিতে ইন্ধন যুগিয়েছে বিধায় বইটি নিষিদ্ধ করণ ও বাজার হতে এর সকল কপি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
আপনার সদয় অবগতি এবং যথাসমীচীন কার্যক্রমের জন্য প্রেরিত হল।
কোত্থেকে প্রেরিত হল? প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর থেকে। ১৩০০/১৬৪/ডি/সি.আই.বি। তারিখ, আষাঢ় ১৪০০/ ০৩ জুলাই,১৯৯৩
এ চিঠি লেখার পর সাতদিনের মধ্যেই লজ্জা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার বইয়ের বাজারে যত লজ্জা পাওয়া গেছে, সব তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। কেবল তাই নয়, স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিশেষ দল বাংলাবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে যত লজ্জা ছিল, সব লজ্জা ট্রাক ভরে নিয়ে গেছে, এমনকী ৬ নম্বর ওয়াল্টার রোডে বই বাঁধাই এর দোকানে গিয়ে আধ-বাঁধানো আর না বাঁধানো বইগুলোকেও রেহাই দেয়নি। কেবল ঢাকায় নয়, দেশের সমস্ত বইয়ের দোকানে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে যত লজ্জা ছিল, পুলিশ সবই বাজেয়াপ্ত করেছে। বই বেরিয়েছে সেই ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রকাশের পাঁচ মাস পর বই নিষিদ্ধ। এর মধ্যে ষাট হাজার বিক্রি হয়ে গেছে। সপ্তম সংষ্করণ চলছিল। আর এখন কী না বইটি নিষিদ্ধ হল! এই সরকার কাকে পড়তে দিতে চায় না বইটি। স্বৈরাচারী সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ বছরের পর বছর রক্তক্ষয়ী আন্দোলন করে স্বৈরাচার উৎখাত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল, আর এই কি না গণতন্ত্রের চেহারা!
কবি শামসুর রাহমান লজ্জা বাজেয়াপ্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। পত্রিকায় কেবল বিবৃতি দিয়েই তিনি দায়িত্ব শেষ হয়েছে বলে মনে করেননি, ভোরের কাগজে লিখলেন, ‘তসলিমা নাসরিন প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। তাঁকে আক্রমণ করা হচ্ছে বহুদিন থেকে। একটি কি দুটি ইসলামী সংগঠন তাঁর ফাঁসির দাবি জানিয়েছে। সরকারকে বলেছে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্যে। সরকার তাঁকে গ্রেফতার করেনি কিন্তু বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাঁর লোকপ্রিয় উপন্যাস লজ্জা। উপন্যাসটি আমি আদ্যেপান্ত পড়েছি। নান্দনিক দিক থেকে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করলেও আমার কাছে এই উপন্যাসের কোনও কিছুই আপত্তিকর মনে হয়নি। তসলিমা নিদ্বির্ধায় সত্য প্রকাশ করেছেন এবং সত্য প্রকাশ করাই একজন লেখকের প্রধান কর্তব্য। তসলিমা নাসরিন একজন মুক্তমতি, অসাম্প্রদায়িক লেখক। কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেওয়ার প্রবণতা তাঁর মধ্যে থাকতেই পারে না, পাঠকদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা থেকেই নিজেকে তিনি বিরত রেখেছেন সবসময়। কোদালকে কোদাল বলতেই পছন্দ করেন তিনি। যা বলেন, সাফ সাফ বলেন, রেখে ঢেকে কিছু বলেন না। এক যুবক আমাকে কিছুদিন আগে জানিয়েছেন যে লজ্জা উপন্যাসটি পড়ে তাঁর মনে হয়েছে যেন তিনি নিজেই উপন্যাসটির নায়ক সুরঞ্জন। এ রকম একটি বই বাজেয়াপ্ত করার যৌক্তিকতা কোথায়? যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি ডক্টর আহমদ শরীফ। তিনি বলেছেন, লজ্জায় তথ্যের কোনও বিকৃতি নেই।
জনগণের রায়ে নির্বাচিত সরকার দেশে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার কথা প্রায়শই বলে। কে না জানে, বাক স্বাধীনতা গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত। অথচ সরকার একজন সৃজনশীল লেখকের বই বাজেয়াপ্ত করে বাক স্বাধীনতা হরণ করেছে। অথচ একটি বই, যা তসলিমা নাসরিনকে হত্যা করার জন্যে সাধারণ মানুষকে প্ররোচিত করছে, বাজারে অবাধে বিক্রি হচ্ছে। কাউকে হত্যার প্ররোচনা দেওয়া মস্ত অপরাধ। এই বইয়ের দিকে সরকার নজর দিচ্ছে না কেন? মৌলবাদীদের বই বলে?
ব্যক্তিগত ভাবে আমি কোনও বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পক্ষপাতি নই। কারণ, আমি মনে করি না কোনও বইই সমাজের ক্ষতি করতে পারে। যে বই মানুষকে হত্যা করতে প্ররোচণা এবং উৎসাহ জোগায়, ফ্যাসিবাদের গুণ গায়, সে বইয়ের কথা আলাদা। যে দেশে ওষুধেও ভেজাল দেওয়া হয়, চোরাচালান কায়েম রয়েছে, খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত করা হয় ভেজাল মিশিয়ে, যে দেশে ক্ষতিকর লোকদের অবাধ বিচরণ, সে দেশে একজন সত্যান্বেষী মুক্তমতি লেখকের বই নিষিদ্ধ করা হয় কেন? একজন লেখক নিরীহ বলেই কি? তসলিমা নাসরিনর লজ্জা উপন্যাসটিকে মুক্ত ঘোষণা করার জন্য আমরা যারা লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাঁরা সরকারের কাছে দাবি জানাই। আশা করি, সরকার লজ্জার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে প্রমাণ করবেন যে প্রকৃতই তারা বাকস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।’
১৯ জুলাই তারিখে লেখাটি ছাপা হয় ভোরের কাগজে। তার পরদিনই ছাপা হল প্রাক্তন বিচারপতি কে এম সোবহানের লেখা। বাজার থেকে লজ্জা তুলে নেওয়ার জন্য সরকার যে বিপুল পুলিশবাহিনী নামিয়েছে দেশে, তা দেখে তিনি মন্তব্য করেছেন ..‘এই পুলিশী তৎপরতা যদি চালানো হত গত ডিসেম্বরের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তা হলে হয়ত বইটি লেখার দরকারই হত না। বইটিতে যেসব বক্তব্য আছে তা বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে উস্কানিমূলক বলে কোনও পাঠক মনে করবেন না যদি না সেই পাঠক ঐ সন্ত্রাসীদেরই একজন বা তাদের প্রতি সহানূভূতিসম্পণ্ন হয়।’
কে এম সোবহান ‘সরকারের লজ্জা ধর্মীয় চরমপন্থীরাঞ্চ এই শিরোনামে আরও একটি কলাম লিখেছেন। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের সঙ্গে ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী দলের যে গলায় গলায় মিল আছে একটি ব্যপারে, তা বলেছেন। জ্ঞস্বৈরাচারী সরকারের ওপর মৌলবাদী চরমপন্থীদের প্রভাবের কারণে ও তাদের উস্কানিতে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চালানো হয়েছিল। স্বৈরাচারী সরকারের অন্যান্য কাজের প্রতি সরকারি দলের অসন্তুষ্টি থাকলেও ঐ কাজটি তাদের পছন্দসই ছিল কেন না স্বৈরাচারীর সঙ্গে এখানে তাদের মতের সম্পূর্ণ মিল। তাই গ্লানি নামের সংকলনটি নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই লজ্জা নিষিদ্ধ।’ বর্তমান সরকার নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছে। কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হলেই, কে এম সোবহান বলেছেন, ‘গণতান্ত্রিক হওয়া যায় না।’
এই যে ধুম করে বইটি নিষিদ্ধ করে দিল সরকার আর এই যে গতমাসেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে গিয়ে বলে এলেন, যে ‘আমাদের রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে এবং সেই কারণে এর অংশ হিসেবে মানবাধিকারের নীতিগুলোর প্রতিও সরকার অনুগত। এটা আমাদের সংস্কৃতি ও সংবিধানের অংশ। আমাদের দেশে গণতন্ত্র কার্যকরী হয়েছে এবং আমাদের কাজে আছে পূর্ণ য়চ্ছত!। সরকার জনগণ ও সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। প্রেস সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এবং বিরোধী দল তাদের অবস্থানে দৃঢ়। সেই কারণে আমরা নীতিগতভাবে মানবাধিকার পালন করব। ..’ এই কি পালন করার নমুনা! কথা এবং কাজের মধ্যে আদৌ কি কোনও মিল আছে এই সরকারের! সংবিধানে যে বেশ স্পষ্ট করে লেখা আছে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কথা, প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের কথা! তা কে মানে! কে দেখে সংবিধান। সরকারি দল মনে করে রাষ্ট্র তারা দখল করে নিয়েছে। ইচ্ছে করলেই তারা ডাংগুলি খেলতে পারে রাষ্ট্রের নীতি নিয়ে। সংবিধানকে সঙ সাজিয়ে রাস্তায় ন্যংটো করে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে ইচ্ছে করলেই। কে এম সোবহান ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, ‘দেশের সবোগচ্চ আইনের সংবিধানে এই বিধান থাকা সত্ত্বেও সরকারের একটি বিভাগ মৌলবাদী ও চরমপন্থীদের প্ররোচনায় বইটি বাজেয়াপ্ত করেছে। এই মৌলবাদী দলটি ও ধর্মীয় চরমপন্থীরা সরকারি দলের কাঁধে সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে বসেছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ আজ এই মৌলবাদী ও ধর্মীয় চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে। তা থেকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও দূরে নেই। মিশর, তুরস্ক, আলজেরিয়া, তিউনেশিয়া, মরককো সর্বত্রই এদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কেবল বাংলাদেশের সরকারি দল ক্ষমতায় আসার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই তাদের কথামত কাজ করছে। মৌলবাদী এই দলটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করছে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য। সরকারকে এটা বুঝে এই মৌলবাদী দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। সরকারগুলোর দূর্বলতার কারণেই সম্ভব হয়েছিল গত ডিসেম্বরে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস করা। তসলিমা নাসরিনকে তাঁর পাঠকবর্গ অভিনন্দন জানাবেন এই মৌলবাদী ও চরমপন্থী ও তাদের ধারককে জনগণের সামনে চিহ্নিত করার জন্য।’
অভিনন্দন আমার জোটে কিছু। তার চেয়েও বেশি জোটে অভিসম্পাত। অভিযোগের শেষ নেই। মুসলমানদের বারোটা বাজিয়েছি, মুসলমান হয়ে মুসলমানের দুর্নাম করেছি, বাংলাদেশে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নেই, যা লিখেছি মিথ্যে লিখেছি, হিন্দুরাই তাদের অবস্থার জন্য দায়ী, সামান্য ধমকেই কোঁচা তুলে ভারতে পালায়, আমার কাণ্ডজ্ঞান নেই, হিন্দুদের হাতের পুতুল হয়েছি, হিন্দু মৌলবাদীরা আমাকে পুরস্কার দিয়েছে, তারা আমাকে দিয়ে লজ্জা লিখিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মৌলবাদীরা তো বলেই কিন্তু বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত আহমদ ছফা বললেন, ‘লজ্জা একটি ইতরশ্রেণীর উপন্যাস।’ এই বইটি ভারতে তাঁর জাতভাই মুসলমানদের বিপদ ঘটাবে বলে তাঁর বিশ্বাস, সুতরাং তিনি জাতভাইদের যেন কোনও বিপদ না ঘটে তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করছেন। লিখেছেন ‘তসলিমা সবসময় মন্দ অংশটাকেই বড় করে দেখে। তসলিমার লজ্জাকে নর্দমার জরিপকারী রিপোর্ট মনে হয়েছে। তার বাকি উপন্যাসগুলো ইতর শ্রেণীর রচনা। ভদ্রলোকের স্পর্শের অযোগ্য।’ হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, ‘তসলিমার লেখা অত্যন্ত নিম্নমানের.। তার লেখা অনেকাংশে অসততাপূর্ণ পুনরাবৃত্তিতে ভরা এবং বাজারের মুখ চেয়ে লেখা।’
কিন্তু সবকিছুর পরও স্বস্তি হয় যে অনেক লেখকই প্রতিবাদ করছেন বই নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে। আবদুল গাফফার চৌধুরীর সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি, আলাপ হয়নি। লন্ডনে বসে কলাম লেখেন তিনি। ভোরের কাগজে কলাম লিখলেন ‘তসলিমার সাহিত্য, বক্তব্য ও মতামতের সমালোচনা নয় বরং ব্যক্তি তসলিমাই সবার আলোচনার বিষয়ঞ্চ, এই শিরোনাম দিয়ে। আমার ব্যক্তিজীবন, আনন্দ পুরস্কার পাওয়া, লজ্জা লেখা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যা ঘটেছে দেশে, সেসব নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন, ‘..তসলিমা নাসরিনের লেখা নিয়ে কোনও বিতর্ক নয়, বিতর্কের নামে আসলে যা শুরু হয়েছে, তা তসলিমার বিচার সভা। এই বিচারসভার স্ব-নিযুক্ত বিচারক হিংস্র এবং ঘাতক মৌলবাদীরা। পেছনে তাদের মদদদাতা ক্ষমতাসীন সরকার। আর জুরির আসনে বসা আমাদের সেক্যুলার ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের একাংশও দ্বিধান্বিত এবং দ্বিধাবিভক্ত। তাঁদের কারও লেখা পড়ে মনে হয়, তসলিমার প্রতি তাঁদের কারও রয়েছে ব্যক্তিগত অসূয়া, কারও রয়েছে আনন্দ পুরস্কার না পাওয়ার অব্যক্ত হতাশা ও ক্ষোভ, কারও রয়েছে তসলিমাকে হেয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দানের চতুর বাসনা। তাই তাঁদের লেখায় বিষয়ের চাইতে ব্যক্তি বড় হয়ে উঠেছে, একটি সুস্থ বিতর্কের বদলে গ্রাম্য বিচারসভার মোড়লপনাই বেশি প্রকট হয়ে পড়েছে।
আনন্দবাজার পত্রিকার বর্তমান ভূমিকা সাম্প্রদায়িক নয়, এদের বর্তমান ভূমিকা গণতান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক মুনাফার। বাংলাদেশের একটি জাতীয় সংস্থা হিসেবে বাংলা একাডেমি কলকাতার একটি ব্যক্তিগত প্রকাশনা সংস্থার অর্থ সাহায্য গ্রহণ না করে ভাল করেছেন, তাই বলে ঢাকার কোনও শিল্পী বা সাহিত্যিকের এই পুরস্কার গ্রহণ না করার কোনও অর্থ হয় না। আনন্দ পুরস্কার প্রদানে পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নেই। তসলিমার নির্বাচিত কলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে মুসলমান ও হিন্দু উভয় ধর্মের বিধানকেই আক্রমণ করা হয়েছে। আনন্দ পুরস্কার সম্ভবত এই অসাম্প্রদায়িক সাহসিকতাকেই পুরস্কৃত করেছে, কেবল বইটির সাহিত্য মূল্যকে নয়।
যে সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্য কোনও আন্দোলন, সংস্কার বা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাতে সবসময় চিরায়ত সাহিত্যের কাঙ্ক্ষিত শিল্পগুণটি থাকে না। যে নাজিম হিকমত বা মায়াকভস্কিকে নিয়ে আমরা এত হৈ চৈ করি, তাদের অধিকাংশ রাজনৈতিক কবিতার শিল্প মূল্য আছে কি?.তসলিমা নাসরিনের লজ্জা উপন্যাস সমাজের একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের তাৎক্ষণিক সাহসী সাহিত্য কর্ম। তাতে বনেদী সাহিত্যের স্থায়ী প্রসাদগুণ আমাদের বুদ্ধিজীবীরা আশা করেন কিভাবে? বিজেপি তসলিমা নাসরিনের লজ্জা উপন্যাসকে তাদের রাজনৈতিক প্রচারণার স্বার্থে ব্যবহার করেছে, এটাও নাকি তসলিমার অপরাধ। সম্প্রতি লন্ডনে বিজেপির একটি ছোট প্রচার পুস্তিকা আমার হাতে এসেছে । নাম বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন, তাতে বিজেপির কোনও নিজস্ব বক্তব্য নেই। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও মন্দির ভাঙার ছোট বড় পঁচিশটি খবর হুবুহু পূণর্মুদ্রণ করা হয়েছে। এই পত্রিকাগুলোর মধ্যে মাওলানা মান্নানের ইনকিলাবও রয়েছে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে এই পত্রিকাগুলো বিজেপির প্রচারপত্র অথবা বিজেপির টাকা খেয়ে এই খবরগুলো ছেপেছে! বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন রোধে বর্তমান সরকারের ইচ্ছ!কৃত ব্যর্থতায় আমাদের বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ যত না লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ, তার চাইতে বেশি লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ তসলিমা লজ্জা উপন্যাস লেখায়। সেলুক্যাস, কি বিচিত্র এ বঙ্গ দেশ।’
বিরানব্বই সালের আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম থেকে বেরিয়েছিল গ্লানি নামের একটি সংকলন। গ্লানিতে ছিল নব্বইয়ের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের কিছু চিত্র, ভাঙা মন্দিরের ছবি আর হিন্দুদের ওপর মৌলবাদীদের নির্যাতনের কিছু তথ্য। সেই গ্লানি নিষিদ্ধ করল সরকার। লজ্জাও নিষিদ্ধ হল। সেলিনা হোসেন, নামী লেখক, লিখেছেন গ্লানি এবং লজ্জা নিয়ে। ‘দুটো বইয়ের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে এগুলো পাঠকের মনে সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে ইন্ধন যোগাবে। অতএব, বই দুটো পাঠকের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেল। ভাবখানা এই যে, এই বইদুটো লুকিয়ে রাখলেই দেশের অস্থিতিশীল সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
জাতীয় কবিতা উৎসব ৮৯ এর শ্লোগান ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা। ঘোষণায় বলা হয়েছিল, আমরা বিশ্বাস করি কবিতার জন্ম ঘটে প্রীতি আর মানবিকতা থেকে, কবিতা কোনও সম্প্রদায় স্বীকার করে না। .. এখন মানবিকতার, অসাম্প্রদায়িকতার কাল। আমরা আমাদের প্রতিটি পর্ব ও পংক্তি, প্রতিটি উপমা উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, আমাদের স্বর, আমাদের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করি অসাম্প্রদায়িক মানুষের নামে, যাঁরা রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানবিকতার অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়াবেন।
এই সাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনাই এই ভূখণ্ডের মানুষের অহংকার। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে বর্তমান বাংলাদেশের সরকারের যা ভূমিকা তা একদিকে যেমন গ্লানিকর, তেমনি লজ্জাজনক। সরকার নিজের অজান্তেই গ্লানি এবং লজ্জা শব্দদুটো নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। সরকার চাইলেই এই গ্লানি এবং লজ্জা হতে মুক্ত হতে পারবে কি?’
লজ্জা নিয়ে আমার যে লজ্জা আর গ্লানি ছিল, ছিল এই কারণে যে উপন্যাস বলতে এটি কিμছু হয়নি, সেটি খানিকটা দূর হয় বুদ্ধিজীবিরা যখন কলম ধরলেন বইটির পক্ষে। ডঃ মুহম্মদ আনিসুল হক লিখেছেন, ‘তসলিমা নাসরিনের লজ্জা বইটি আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক পাশবিকতার বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। .. এই বই স্বভাবতই এদেশে কারও কারও গাত্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষত যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জঘন্যতম ভুমিকায় লিপ্ত হয়েছে তারা তো ক্ষেপবেই। প্রকৃতপক্ষে সত্য চিরকালই সত্য। সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করলেই সত্য মিথ্যে হয়ে যায় না।’ নিজে তিনি একদিন বাড়িতে এসে তৃতীয় ধারা দিয়ে গেলেন, যে পত্রিকাটিতে লেখাটি ছাপা হয়েছে। যাবার সময় বললেন, ‘আজ বসনিয়ায় সার্বরা মসজিদ ভাঙাছে, আমাদের মৌলবাদিরা এখন কি এদেশের কোনও গির্জা ভাঙতে যাবে? যাবে না। সরকারও দেবে না গির্জা ভাঙতে, কারণ তাহলে তো ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নাখোশ হবে।’
হাসান ফেরদৌস একজন সাহসী সাংবাদিক। আমেরিকায় থাকেন। নিয়মিত বাংলাদেশের কাগজে লেখেন তিনি। তিনিও লিখলেন, ‘বইকে গলা টিপে হত্যা করা যায় না। কিন্তু নিষিদ্ধ করা যায়, পুড়িয়ে ফেলা যায়। বই যে সত্যকে উদ্ধার করে, তা নিয়ে যখন সন্ত্রস্ত হয় কেউ, তাকে নিষিদ্ধ করার, তাকে পাঠকের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। সত্যের মুখোমুখি হবার চাইতে তার টুঁটি টিপে রাখা, তাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা অনেক সহজ, তাই। ক্ষমতাধর মানুষ ও তাদের সমাজ এই চেষ্টা করেছে চিরকাল। চেষ্টা করেছে, পারেনি। সক্রেটিসকে হত্যা করা গেছে, কিন্তু যে সত্য তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, তাকে লুকিয়ে রাখা গেছে কি? বইএর বহ্নুৎসব করেছে হিটলার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে সে নিজে। লজ্জা কেবল বিরানব্বই এর দাঙ্গার কাহিনী নয়। এটি বাংলাদেশে সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতার একটি প্রামাণ্য দলিল।’
যতীন সরকার আজকের কাগজ পত্রিকায় কলাম দীর্ঘ কলাম লিখলেন লজ্জার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি নিয়ে। লিখেছেন, ‘লজ্জা বাজেয়াপ্ত করে তাঁরা নিজেদের লজ্জাহীনতার অকুণ্ঠ প্রমাণ রাখলেন। লিখেছেন বে আইনি কাজ তাঁরা করেননি। বই বাজেয়াপ্ত করার আইন তাদের আছে। এই আইন তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছ থেকে। সেই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে দেশের মানুষ প্রাণ দিয়েছে, মান দিয়েছে এবং এ রকম বহু ত্যাগের বিনিময়ে ঔপনিবেশিকতা দূর করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আবার সেই স্বাধীনতাও যখন স্বৈরাচারিতার নিগড়ে বন্দী হয়ে গেছে, তখন তার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যও মানুষকে রক্ত দিতে হয়েছে। এরপর স্বৈরাচারমুক্ত দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণসমর্থন নিয়ে যাঁরা ক্ষমতায় এলেন, তাঁদের হাতেও শাসনের হাতিয়ার রূপে সেই স্বৈরাচারীদের আইনগুলোরই ব্যবহার ঘটে। বলা উচিত, অপব্যবহার ঘটে। এখানেই দেশের জনগণের লজ্জা। অথচ, জনগণের মাথার ওপর শাসক হয়ে বসে আছেন যাঁরা, তাঁদের কোনও লজ্জা নেই। লজ্জা যদি থাকতো, তবে ঘৃণ্য উপনিবেশবাদী ও স্বৈরাচারীদের তৈরি আইনের প্রতি তাঁদের ঘৃণাও থাকতো। এবং থাকতো জনমতের প্রতি ভয়ও।’
লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়— এই মন্ত্রটি শাসকেরা ঠিক ঠিক রপ্ত করে নিয়েছেন। তাই ‘সেই মানবিক লজ্জা, পবিত্র ঘৃণা ও মহৎ ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকলে ঔপনিবেশিক পূর্বসুরিদের অন্যায় আইন ব্যবহার করে কোনও লেখকের বই বাজেয়াপ্ত তো তাঁরা করতেনই না, বরং সে সব আইনেরই উচ্ছেদ ঘটিয়ে বিবেকী লেখকের লেখার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতেন কিন্তু তেমনটি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ লজ্জার মানবিকতা, ঘৃণার পবিত্রতা ও ভয়ের মহত্ত্বকে ধারণ করার মত হৃদয় তাঁদের নেই। আমরা আগেই দেখেছি, লজ্জা ঘৃণা ও ভয়কে তাঁরা বহু পূর্বেই জলাঞ্জলি দিয়েছেন। তাই, অপরের লজ্জাও তাঁরা সহ্য করতে পারেন না।
লজ্জা আমার লজ্জা নয়, এটি আসলে জাতির লজ্জারই ভাষারূপ। এত বড় একটি কথাও তিনি লিখেছেন। যতীন সরকার বিশ্বাস করেন না বাঙালি কোনওকালেই সাম্প্রদায়িক কোনও জাতি। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়সত্তার অবিচ্ছেদউ অঙ্গে পরিণত করে নিয়েছে। কিন্তু সকল জাতির মধ্যে চাঁদের কলংকের মত কিছু কুলাঙ্গার থাকে, বাঙালি জাতির মধ্যেও এরা ছিল ও আছে। এই কুলাঙ্গাররা স্বাধীনতা সংগ্রামেও জাতির বিরোধিতা করেছিল। স্বাধীনতার পরও এরা প্রতিনিয়ত জাতির মুখে কলঙ্ক লেপন করতে ব্যস্ত। এরা সংখ্যায় নগণ্য। এই সংখ্যালঘু দুর্জনদের ঘৃণ্য কার্যকলাপই সংখ্যাগুরু সজ্জনদের তথা সমগ্র জাতিকে কলঙ্কিত ও লজ্জিত করেছে।’
লজ্জা লিখে সেই কলঙ্ক ও লজ্জা মোচন আমি কতটুকু করতে পেরেছি! ভাবি। যে গল্প আমি লিখেছি, সে গল্প তো সকলেই জানে। এ তো নতুন কিছু নয়। অনেক বলা অনেক জানা কথাগুলোই আমি বলেছি। যে ভাবনাগুলো প্রতিদিন ভাবি, যে কথাগুলো আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে সকাল সন্ধে বলছি, যে প্রতিবাদগুলো ব্যক্ত করছি, যে ক্ষোভগুলো প্রকাশ করছি প্রতিদিন, যে প্রতিরোধের আগুনগুলো ঝরছে আমাদের হৃদয় থেকে, লজ্জাতে তার অতি সামান্যই প্রকাশ পেয়েছে। আমি জানি, আমার প্রগতিশীল বন্ধুরা জানেন, আমাদের সামনের পথটি কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু জানি আমরা থেমে থাকলে পথে আরও কাঁটা জমা হবে, পথ আরও বন্ধুর হবে। জানি ও পথে আমাদের যেতেই হবে, যে পথে সাহস নেই সবার যাবার। কারও সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে আমাদের আপোস করলে চলবে না। এখন স্পষ্টতই দুটি পক্ষ। একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল, আরেকদিকে প্রগতিশীল। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সমাজকে পিছিয়ে দিতে চায় হাজার বছর। অন্ধতা কুসংষ্কার, হিংসা,বিদ্বেষ, ভয় ভীতি ছড়িয়ে দিতে চায় মানুষের মধ্যে। প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত শক্তিশালি করতে সাহায্য করছে আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার। তাদের হাতে আছে অস্ত্র আর অর্থ। আমাদের শূন্য হাত। কিন্তু বিশ্বাসে পূর্ণ হৃদয়। সমতা আর সাম্যের বিশ্বাস।
এদিকে প্রতিদিনই মৌলবাদিদের পত্রিকায় আমাকে দেশদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী বলে গাল দেওয়া হচ্ছে। মৌলবাদিরা গাল দেবেই জানি, কিন্তু মৌলবাদি নয় বলে যারা দাবি করে, প্রগতিশীল মুখোশ পড়ে আমাদের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করে, তাদের কিছু কিছু মুখকে আমরা চিনতে পারছি, নতুন করে, আরও গভীর করে চিনছি। ফরহাদ মজহার আর আমহদ ছফা দিব্যি লজ্জাকে দোষ দিয়ে লিখেছেন, ‘লজ্জা দুইবাংলার মানুষদের মিলনের মধ্যে বাঁধা। খোঁচা দিয়ে দাঙ্গা বাঁধাবার মত পরিবেশ সৃষ্টি করছে।’ আর ফরহাদ মজহার তো আরও কয়েককাঠি এগিয়ে গিয়ে বলে দিলেন, ‘কলমের এক খোঁচায় বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানিয়ে ফেললাম, আর আজ আমরাই হিন্দু ভারত নিয়ে উদ্বিগ্ন। যদি খতিয়ে দেখি তাহলে দেখবো বাবরি মসজিদ ভাঙার শর্ত তৈরি করে দেবার পেছনে অনেকাংশে আমরাই দায়ি।’ বিজেপি, ভারতের হিন্দুবাদী দল, তাঁর ধারণা ‘কিছ কিছু বাংলাদেশীদের দিয়ে বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়ার ফোলানো ফাঁপানো বিবরণ দিয়ে উপন্যাস কাহিনী গল্প গুজব রচনা করাচ্ছে।’ ঠিক এই দোষটিই আমাকে দিচ্ছে মৌলবাদিরা। বিজেপি নাকি আমাকে টাকা দিয়ে লিখিয়েছে লজ্জা। ফরহাদ মজহারের মত লোকের অভাব নেই দেশে, তাঁর আবার কিছু উচ্চশিক্ষিত ভক্তবৃন্দ বিরাজ করছে। মাশআল্লা। শিবনারায়ণ রায় বলেছেন, ‘মুখোশের আড়ালে আমরা সবাই নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত স্বধর্মপ্রাণ। শিক্ষিত বাঙালি নিজেকে আধুনিক বলে দাবী করলেও তার জীবন ও ইতিহাসে এই স্বীকৃতির চিহ্ন দুর্লভ। বাঙালি আজও তার হিন্দুত্ব ও মুসলমানিত্ব অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের পরিজ্ঞান অর্জন করেনি।’ কথাটি সফি আহমেদও মানেন। কী আশ্চর্য স্বীকারোক্তি সফি আহমেদের, তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন, ‘সাম্প্রদায়িকতার এই গলদ আমাদের প্রায় সবার। এই দগদগে ঘা কে ঢেকে রাখলেই অথবা নেই বললেই তাকে অনস্তিত্বে আনা যায় না। তাকে স্বীকার করার সৎ সাহস থাকা চাই। অসুখকে জেনে নিয়েই তবে চিকিৎসা। সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আমাদের জন্ম। তারপর আজ ছেচল্লিশ বছর আমরা তারই ভেতর দিয়ে চলেছি, চেতনে অচেতনে তার ভেতরেই বহমান। শুধু ক্ষমতাশীল শোষকের শোষণের হাতিয়ার হিসেবেই নয়, মুখোশের আড়ালে আমরা প্রায় সবাই একে পোষণ করি, লালন করি।’
এরপরই লজ্জা প্রসঙ্গে বললেন, ‘কখনও যদি একে ধরে টান দেয়, খুলে দেয়, কোনও অকুতোভয় প্রাণ যদি বন্ধ অর্গল মুক্ত করে তাকে স্বাগত জানাই। উন্মোচন করেই লুকোনো লজ্জাকে নির্ভার নির্মল করতে হবে। লজ্জা দাঙ্গা আনবে না, বরং লজ্জাই আমাদের মেলাবে।’
যখন সরকারের খড়গ আমার ওপর খাড়া, তখন আমার পক্ষে বা লজ্জার পক্ষে লেখালেখি করা খুব সহজ কথা নয়। তারপরও সাহস করে অনেকে লিখছেন, যাঁরা লিখছেন না, হয় তাদের আমাকে পছন্দ নয়, নয়ত আমার লেখা পছন্দ নয়, নয়ত লজ্জার বক্তব্য পছন্দ নয়। তা হতেই পারে। আমার নিজের কাছেই আমার অনেক লেখা পছন্দ হয় না। লজ্জার বক্তব্য পছন্দ হলেও লজ্জা লেখার ধরণ আমার নিজেরই পছন্দ নয়। ঠিক এই কাহিনী নিয়ে খুব হৃদয়স্পর্শী একটি উপন্যাস লেখার সুযোগ ছিল। চরিত্রগুলোকে আরও মানবিক করা যেত। উপন্যাসের কোনও গভীরতা, কোনও বিপুলতা এই বইটিতে নিয়ে সে আমি জানি। জানি বলেই বইটি নিয়ে কারও কারও অতীব প্রশংসা আমাকে যেমন লজ্জা দেয়, তেমনি প্রেরণাও দেয়। নিজের শক্তি আর সাহসকে হারিয়ে না ফেলে আরও ভাল কিছু লেখার প্রেরণা। যদি দম্ভ আমাকে বিবেকহীন বানাতো, যদি আত্মম্ভরিতা আমাকে অন্ধও করে দিত, তবুও আমার মনে হয় না আমি কখনও ভাবতে পারতাম যে আমার এই সামান্য বইটি একদিন সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে খোঁজ করবে কেউ বা এই বইটি মানরক্ষা করবে জাতির। আমার বিশ্বাস আমার সম্পর্কে বা আমার বইটি সম্পর্কে অনেকে বাড়িয়ে লিখছেন, সম্ভবত বইটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে অথবা আমার ওপর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর আক্রমণ খুব তীব্র বলে। বশীর আল হেলালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। তিনি দেশের একজন প্রথিতদশা সাহিত্যিক। তাঁর একটি লেখা আমাকে সত্যিই চমকে দেয়। ‘হিন্দু মুসলমানের, মুসলমান হিন্দুর কথা লিখবে, এই তো স্বাভাবিক। সরকার কি মনে করেছেন এতে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়? না, ক্ষতি হয় না, লাভ হয়। ভারতে মুসলিম নির্যাতন হলে তখন আমরা দেখাতে পারব, দেখ, আমাদের লেখক আমাদের হিন্দুদের নিয়ে এই উপন্যাসখানা লিখেছেন। এই তো গৌরব, এই তো মনুষ্যত্ব। শাক দিয়ে মাছ তো ঢাকা যায় না, কিছুতেই যায় না। সাহিত্যের ইতিহাস লেখার সময় এই রকম বইয়েরই তো খোঁজ পড়বে। তসলিমা নাসরিন এ উপন্যাসখানা লিখেছেন বলেই না সেদিন মানরক্ষা হবে। নিষেধের সব অন্ধকার ভেদ করে এই উপন্যাসখানাই সেদিন মুখ উজ্জ্বল করে বেরিয়ে আসবে। আমি বলব, তসলিমা নাসরিন অসাধারণ একখানা উপন্যাস লিখেছেন এই লজ্জা। এ রকম আর এ দেশে লেখা হয়নি। বড় তীব্র এই উপন্যাস। আঘাত করে, কঠিন আঘাত করে। তবে, সত্য যা তাই তিনি লিখেছেন। কারো পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু এ সত্য, নিষ্ঠুর সত্য। সত্যপ্রীতির জন্য এই লেখকের ভোগান্তি হবে বলেই মনে হয়।’
ওদিকে লজ্জা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। লজ্জার নকল বই বেরিয়ে গেছে। হাটে বাজারে ট্রেনে বাসে দেদারসে বিক্রি হচ্ছে। ওখানেও লেখালেখি হচ্ছে লজ্জা নিয়ে। মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর যে নির্যাতন চলে তার বর্ণনা দিয়ে প্রশ্ন করেছেন কেন ভারতবর্ষে লজ্জার মত বই ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিয়ে রচিত হয়নি। তাই লজ্জা তসলিমার নয়, লজ্জা ভারতবাসীর। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের এক মন্ত্রী বলেছেন, ‘তসলিমার লজ্জাকে কোনও অবস্থাতেই বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবা ঠিক হবে না।’ পশ্চিবঙ্গের কমিউনিস্টরা ওখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানের ওপর যেন কোনও বিপদ না হয়, সে ব্যপারে সতর্ক। মুসলমান-প্রেম তাদের যত না আছে, তার চেয়ে বেশি আছে মুসলমান- ভোটের মোহ। লজ্জা বইটিকে মিথ্যে বলেও যদি পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, আমি বরং খুশীই হব। কমিউনিস্টদের মন্তব্যে আমার মন খারাপ হয় না। আমার মন খারাপ হয় যখন তাঁরা বলেন যে আনন্দবাজার গোষ্ঠী নয়ত বিজেপি আমাকে দিয়ে মুসলমান বিরোধী বই লিখিয়েছে। বইটি আমি বুদ্ধদেব গুহকে উৎসর্গ করেছি, এ নিয়েও আমাকে নিন্দা করা হচ্ছে। বুদ্ধদেব গুহ নাকি বিজেপির লোক, বিজেপির মেনিফেস্টো তিনি লিখেছেন। বুদ্ধদেব গুহর সঙ্গে আমার আলাপ আনন্দ পুরস্কার অনুষ্ঠানে। এমন প্রাণচঞ্চল পুরুষ, এমন রঙ্গপ্রিয় রসরাজ, এমন সপ্রতিভ সৌখিন মানুষ খুব চোখে পড়ে না। বুদ্ধদেব আমাকে, তিনি যেখানেই থাকুন, যে নগরে বা যে জঙ্গলেই, নিয়মিত চিঠি লেখেন। চিঠিতে তাঁর জঙ্গল ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা থাকে, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জন্য তাঁর মমতার কথা থাকে। তিনি বিজেপির সমর্থক নাকি সিপিবির, তিনি ধর্মের পুজারি নাকি অধর্মের, কিছুই আমার জানা নেই। তাঁর একটি বই আমাকে উৎসর্গ করেছেন। কোনও লেখক তাঁর কোনও বই আমাকে উৎসর্গ করলেই যে বিনিময়ে আমার বই তাঁকে উৎসর্গ করতে হবে, এরকম কোনও কথা নেই। বুদ্ধদেব গুহর আমি মুগ্ধ পাঠক বলে, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেই তাঁকে আমার একটি বই উৎসর্গ করেছি।
লজ্জার প্রকাশক এসে মুখ চুন করে বসে থাকেন। তাঁর ব্যবসা হচ্ছে না। সপ্তম মুদ্রণ চলছিল লজ্জার। নিষিদ্ধ হওয়ার আগে ষাট হাজারের মত বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু তাতেও আলতাফ হোসেন ওরফে মিনুর দুঃখ যায় না। তিনি এখন এ বঙ্গেও বিক্রি করতে পারছেন না, ও বঙ্গেও রফতানি করতে পারছেন না। লজ্জার পাণ্ডুলিপি পেয়ে মিনুর মুখে হাসি ফোটেনি। মিনুর চুন মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটেছিল মেলায় বই বিক্রি দেখে। সেই আকর্ণ হাসিটি উবে গিয়ে মিনুর মুখটি যথারীতি চুনে ফিরে এসেছে। তিনি বলছেন, ‘বই ত ব্যাণ্ড হইয়া গেল। আমার তো ব্যবসা পাতি কিছুই হইল না। এখন নতুন একটা বই দেন।’
আমি তখন বই দেব কী করে। আমি লজ্জা লিখছি। নতুন করে লিখছি। ঘটনা একই। তথ্য একই। কেবল ভাষার ভুলগুলো সংশোধন করা, আর চরিত্রগুলোকে আরও চলাফেরা করানো, কথা বলানো। কোনও উপন্যাস লিখে আজ পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাইনি। লিখেছি, ছাপা হয়েছে। কিন্তু পাতা উল্টোলেই বানান ভুল, বাক্যের ভুল ভাষার ভুল, বর্ণনার ভুল সব দাঁতকপাটি মেলে ধরেছে। মন খারাপ হয়ে যায়। প্রকাশক যখন ছাপাখানা থেকে বাঁধাই হওয়া তাজা বই খুশিতে নাচতে নাচতে আমার কাছে নিয়ে আসেন, সেই নাচ থেমে যায় আমি দুইএটি পাতায় চোখ বুলোনোর পরই। কারণ আমার তখন চুক চুক লেগেই আছে জিভে। প্রকাশক বলেন, ‘কি কি ভুল আছে, তা সংশোধন করে দেন, নেক্সট এডিশনে ঠিক করে দেব।’
আলতাফ হোসেন মিনু তাঁর চুন-মুখ খানিক পর পর খুলছেন, ‘আজকে খবর পাইলাম নিউমার্কেটের বইয়ের দোকানে লজ্জা বিক্রি হইতাছে। শুধু নিউমার্কেটে না।
বিজ্ঞানমেলায়, রাস্তাঘাটে, নিউজপেপার স্টলে, এমন কী ফুলের দোকানেও। কভার ছাড়া আশি টাকা, কভার নিয়া একশ টাকা।’
‘চল্লিশ টাকার বই একশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে! তার মানে পাঠক ষাট টাকা বেশি দিয়া বই কিনছে? বই ব্যাণ্ড করে তো পাঠকের ক্ষতি হল, আর কিছু না।’ আমি বলি।
‘আপনে আছেন পাঠকের ক্ষতি নিয়া। আমার ক্ষতির কথা ভাবতাছেন না। কলকাতা থেইকা দশ হাজার কপির অর্ডার ছিল। পাঠাইতে পারলাম কই!’
‘এই যে বললেন বই বিক্রি হচ্ছে এইখানে। এরা বই পাইল কি কইরা? আপনে তো বিক্রি করছেন না।’
‘আমি বিক্রি করব? আমার দোকানে দিনে দুইবার কইরা পুলিশ আসতাছে। সব বই তো নিয়াই গেছে। গোডাউন থেইকা নিছে। বুক বাউণ্ডারের কাছে যা ছিল নিয়া গেছে। এখন ত পাইরেট হইয়া গেছে বই।’
‘কলকাতায় শুনলাম পাইরেট হয়েছে। এইখানেও নাকি? ব্যাণ্ড করে তাইলে সরকারের লাভ কি হইল?’
‘যেইদিন ব্যাণ্ড করল বই, তার দুইদিন পরেই পাইরেট কপি বাজারে আইসা গেছে। বাংলাবাজারেই কেউ কেউ পাইরেট ব্যবসা করে। তাদের মধ্যেই কেউ করল কি না! এখনও কিছু খবর পাই নাই।’
‘পুলিশ এখন কি বলে? সরকার তো বই ব্যাণ্ড করল। কিন্তু বই যে ঠিকই বিক্রি হচ্ছে তা এখন দেখে না কেন?’
‘ওরা তো বই সামনে রাইখা বিক্রি করতাছে না। লুকাইয়া রাখে। আস্তে কইরা কানের কাছে মুখ নিয়া চাইলে পরে দেয়। কাগজে মুড়াইয়া দেয়। আমার লোক গিয়া তিনটা পাইরেট কপি কিনে আনছে।’
‘কেউ কেউ বলছে লজ্জার প্রকাশক কেন ব্যানের বিরুদ্ধে মামলা করছে না!’
‘মামলা?’ মিনুর মুখখানা হঠাৎ ছোট হয়ে যায়। পিটপিট করে এদিক ওদিক তাকান। বুঝি, এ মামলা করতে হলে বুকের পাটা যত বড় থাকতে হয়, তত বড় তাঁর নয়।
‘মামলা কইরা কি কোনও কাজ হইব?’ মিনু মিনমিন করেন।
‘হতেও পারে। আর যদি ব্যান না তোলে, তারপরও তো একটা জিনিস ভাল যে আমরা মেনে নেই নাই সরকারের এই আচরণ। কারণ এই আচরণ বাকস্বাধীনতার বিরুদ্ধে, মানুষের মত প্রকাশের বিরুদ্ধে।’
মিনু অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকেন। শব্দ করে চায়ে চুমুক দেন। পরে চা টাও রেখে দেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বলে। এরপর নরম সুরে বলেন, ‘নতুন একটা বই লেইখা দেন।’ ‘নতুন বই? এখন? এখন তো লজ্জার কারেকশন নিয়া ব্যস্ত। এইতো আর দুএকদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।’
‘কয়দিন আর লাগে একটা বই লিখতে! বইবেন, শেষ কইরা উঠবেন। হুমায়ুন আহমেদ কত বই এক রাত্রে লিখছে!’
‘মিনু ভাই, আমি হুমায়ুন আহমেদের মত লিখতে পারি না। এক রাতে আবার বই লেখা যায় নাকি। তাছাড়া লজ্জাটা সংশোধনের কাজ এই তো শেষ হয়ে যাবে। তারপর অন্য বইয়ের কথা ভাবব!’
‘এক বই কতবার লিখবেন! তার ওপর ব্যান্ড বই। লিখতাছেন যে, আমি ত আর ছাপতে পারব না। জানেন ত আমি বই আমদানি রফতানির ব্যবসা বাদ দিয়া প্রকাশনায় নামছি। আমারে ডুবাইয়েন না।’
না, তাঁকে ডোবানোর কোনও ইচ্ছে আমার নেই। আমি কথা দিই নতুন বই লিখব। কেবল কি আলতাফ হোসেন ওরফে মিনু তাড়া দিচ্ছেন! এখন প্রকাশকের চেহারা দেখলে প্রমাদ গুনি। মইনুল আহসান সাবের, ভাল গল্পলেখক, তিনিও দিব্যপ্রকাশ নামে একটি প্রকাশনী দিয়েছেন। বাড়িতে এসেছেন কদিন বই চাইতে।
‘নাসরিন তুমি যদি আমাকে কয়েকদিনের মধ্যে একটা উপন্যাস লিখে না দাও, আমি মারা যাবো।’
এতজনকে কি করে রক্ষা করি। প্রকাশকদের ভিড় দিন দিন বাড়ছে। আমার তো কেবল লেখাই কাজ নয়। সকাল সন্ধে চাকরি। সংসারের সাত রকম ঝামেলা। সাত পত্রিকায় কলাম লেখা। সাপ্তাহিক বৈঠক। অবশ্য এটিকে সাপ্তাহিক বললে ভুল হবে। বৈঠকটি যে কোনও দিন যে কোনও সময় হতে পারে। আমাদের এই আড্ডায় নারী পুরুষ সকলেই আছেন, বয়সের তারতম্য কোনও ব্যপার নয়, সাহিত্যিক অসাহিত্যিক কোনও ঘটনা নয়, পেশা কোনও ঘটনা নয়, কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাত থাকতে পারে, সেও কোনও বিষয় নয়, কে কোন ধর্মের মানুষ সে তো কোনও বিষয়ই নয়, আসলে ধর্মে বিশ্বাসী কেউ আমাদের এই বৈঠক বা আড্ডায় নেই। একটি ব্যপারে আমাদের পরিষ্কার হতে হয় আমরা মৌলিক কিছু বিষয়ে একমত কি না। আমাদের বিশ্বাস আছে কি না গণতন্ত্রে অথবা সমাজতন্ত্রে, ধর্মনিরপেক্ষতায় অথবা সেক্যুলারিজমে, ব্যক্তি স্বাধীনতায়, বাক স্বাধীনতায়, মুক্তচিন্তায়, মুক্ত প্রচারমাধ্যমে, সবার জন্য অন্ন বস্ত্র খাদ্য শিক্ষা স্বাস্থের সুযোগ প্রদানে, সেক্যুলার শিক্ষা প্রসারে, নারী মুক্তিতে, নারী পুরুষের সমানাধিকারে, বৈষম্যহীন আইনে, দারিদ্র দূরীকরণে, দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস দূরীকরণে, সবার জন্য নিরাপত্তা বিধানে, বাঙালিত্বে, বাঙালি সংস্কৃতিতে, সুষ্ঠু রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায়, অন্ধত্ব, গোঁড়ামি কুসংস্কার আর মৌলবাদ নির্মূলে, সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদে। আমাদের আলোচনার বিষয় সবই, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, কখনও কখনও শিল্প সাহিত্য। আমরা কোনও দিন ক্ষণ ঠিক করে রাখি না কখন বৈঠক হবে, আমরা কোনও বিষয় ঠিক করে রাখি না কোন বিষয়ে কথা হবে। যে কোনও বিষয়ে, যখন যার ইচ্ছে আলোচনার ডাক দিতে পারে। কোথায় বসবে এই বৈঠক, তাও নির্দিষ্ট করা নেই। যে কোথাও হতে পারে। আমার যেহেতু স্বামী সন্তানের ঝামেলা নেই, আমার বাড়িটিই একটি চমৎকার জায়গা। আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্দীপনা। আমাদের চোখে সুন্দরের স্বপ্ন। আমরা শঙ্কিত মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর ধীরে ধীরে শক্তিমান হতে থাকায়। আমরা জানি এই অপশক্তিটি আমাদের সর্বনাশ করতে এগিয়ে আসছে। আমরা জানি আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। পূরবী বসু আমেরিকার বড় পদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রাণের টানে চলে এসেছেন নিজের দেশে। এখানে বেক্সিমকো কোম্পানিতে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছেন। অবসরে গল্প লেখেন। আর এখন এই নৈরাজ্যের সময় গল্প লেখক, কী ঔপন্যাসিক কী কবি সকলেই যখন রাজনৈতিক কলাম লিখছেন, তিনিও লিখছেন। বাঙালি সত্ত্বাটি মানুষের যায় যায় করছে বলে তিনি বাঙালি নামে একটি প্রবন্ধের বই সম্পাদনা করলেন, সঙ্গে সাংবাদিক হারুন হাবীব ছিলেন। বাঙালি বেরোনোর পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সফি আহমেদ কে নিয়ে এখনও গেল না আঁধার নামে একটি বিশাল বই সম্পাদনা করছেন। বাবরি মসজিদ ভাঙার পর দেশে যে কটা দিন ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চলেছে, সে বিষয়ে পত্রিকার খবর আর নিবন্ধগুলোর একটি সংকলন। সফি আহমেদ ছায়ার মত থাকেন পূরবী বসুর সঙ্গে। অনেকটা জ্যাঁ পল সাষর্ন আর সিমোন দ্য বোভোয়ার কথা মনে হয় ওঁদের দেখলে। অসাধারণ দার্শনিক বন্ধুতা। ফরহাদ মজহার, যাঁকে একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে ধরা হয়, তিনিই যখন হিন্দুদের ওপর মুসলমানের অত্যাচারকে অত্যাচার বলতে রাজি নন এবং দাবি করেন, এই বাংলার সংষ্কৃতি ইসলাম, এটিকে আমাদের রক্ষা করতে হবে, তখন আমাদের পিলে চমকে ওঠে। মূর্খ দেখলে আমরা ততটা আতঙ্কগ্রস্ত হই না, ধূর্ত দেখলে যত হই। আমরা আরও বেশি তাগিদ অনুভব করি দলবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ করার, শক্তিগুলোকে একত্রিত করার। পূরবী বসু জরুরি তলব করলেন আমাকে। এসবের প্রতিবাদ করতে হবে, চল এক কাজ করি, আজ আমি লিখব, কাল হারুন লিখবে, পরশু তুমি লিখবে, তরশু সফি লিখবেন। আমরা তাই করি। বসে নেই আমরা কেউই, তারপরও মনে হয়, যথেষ্ট যেন কিছু হচ্ছে না। চোখের সামনে সকলেই দেখছে দেশটির গায়ে পচন ধরছে, দেখেও খুব বেশি কেউ পচন সারাবার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে না। আমরা আসলে সংখ্যায় কম। মুখ বুজে থাকা মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি।
লজ্জার সংশোধন শেষ হল খুব দ্রুত। কাজটি হল সম্পূর্ণ শুয়ে থেকে, বিছানায় নয়, মেঝেয় শুয়ে। মেরুদণ্ডে তীব্র ব্যথা হয়েছিল কদিন। হাড়ের ডাক্তার আমার মেরুদণ্ড পরীক্ষা করে পিঠের এক্সরে করিয়ে বলে দিলেন হাঁটাহাঁটি করা নিষেধ, পেচ্ছাব পায়খানায় যাওয়া নিষেধ, তিন মাস মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে হবে, এমনকী ডানে বামে কাত হওয়া নিষেধ। এই হল চিকিৎসা। অসুখটি কি জানতে চাই। অসুখটি হল, আমার মেরুদণ্ড খুব সোজা। এটিই হল অসুখ। এ আমার জন্ম থেকেই। সোজা মেরুদণ্ড নিয়ে জন্মেছি। মেরুদণ্ড সোজা হওয়ার কারণে যখনই আমি উপুড় হই বা মেরুদণ্ড বাঁকা করি, তখনই চাপ লেগে হাড় বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে, একটির তল থেকে আরেকটি। মেরুদণ্ডের হাড় কখনও কারও একটি সরল রেখায় থাকে না, পিঠের নিচদিকে ঢেউএর মত খেলে যায়। কিন্তু আমার মেরুদণ্ডে ঢেউ বলে কোনও ব্যপার নেই। সোজা মেরুদণ্ডের চিকিৎসা চলতে থাকে, চিকিৎসা করে এটিকে অন্য সবার মেরুদণ্ডের মত করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু বেরিয়ে আসতে থাকা হাড়টিকে ভেতরের সরলরেখায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য শুয়ে থাকা। তিন মাস এই চিকিৎসার পর যখন দাঁড়াবো, হাঁটবো, সারাজীবনের জন্য আমার উপুড় হওয়া চলবে না, হাতে ভারী কিছু বহন করা চলবে না, শুতে হলে শক্ত বিছানায় শুতে হবে। সোজা মেরুদণ্ডকে সোজাই রাখতে হবে। টানা তিনমাস শুয়ে থাকার চিকিৎসা মেনে চলা আমার দ্বারা সম্ভব যে হবে না, সে আমি ভাল করে জানি। তবু হাসপাতাল থেকে দু সপ্তাহের ছুটি নিয়ে শোবার ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকি। কমপিউটার মেঝেয় নামিয়ে, উপুড় হয়ে (লেখার অবসরে চিৎ) কীবোর্ড টিপেছি, মেরুদণ্ড বাঁকা হচ্ছে না এটি ছিল সান্ত্বনা। লেখা শেষ হলে কমপিউটার থেকে ছেপে নিলাম পুরো লজ্জা। আগের চেয়ে দ্বিগুণ। লিখে উঠে আমার এক বদঅভ্যেস, পুরো লেখাটা একবারও পড়ে দেখি না। পড়লে একশ একটা ভুল বেরোবে, বিশেষ করে বাক্য গঠনের ত্রুটি, বেরোলেই আবার নতুন করে পুরোটা লিখতে ইচ্ছে হবে। জীবনেও আর কোনও বই শেষ হবে না। লজ্জাকে একটু টেনে লম্বা করে আমার অন্তত একটি স্বস্তি হয়, যে, কিছু তথ্য বিস্তারিত বর্ণনা করা গেল। কিন্তু কলকাতায় পাণ্ডুলিপি পাঠাবো কী করে আমি! আমার বাড়ির সামনে স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুতিনটে লোক দাঁড়িয়েই থাকে। পোস্টাপিসে গেলে পিছু নেবে এরা, নিষিদ্ধ জিনিস পাচার করার অপরাধে জেলে ভরে রাখবে। কলকাতায় কেউ কি নিয়ে যেতে পারে পাণ্ডুলিপিটি! আমার তো দেশ থেকে বেরোনোর কোনও উপায় নেই। পাসপোর্ট আটকে রেখেছে। কে যাচ্ছে কলকাতায়, কে যাবে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে-ই যাচ্ছে লজ্জার পাণ্ডুলিপি নেওয়ার কোনও সাহস কারওরই নেই। এই দুঃসময়ে একজন আমাকে উদ্ধার করলেন, তার নাম মোস্তফা কামাল। মোস্তফা কামাল লোকটি সাদাসিধে। বিস্তর কথা বলেন। তাঁর ভাই ফেরদৌস ওয়াহিদ একজন নামকরা গায়ক। ভাই নাম করলেও মোস্তফা কামাল নাম করেননি কিছুতে। তাঁকে আমি প্রথম দেখি কলকাতায়। আবৃত্তিলোকের অনুষ্ঠানের পর খাওয়া দাওয়ার উৎসব হচ্ছিল কেনিলওয়ার্থ হোটেলে, সেখানে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রথম দেখা কোট টাই পরা কামাল আমার বাড়িতে টিশার্ট স্যাণ্ডেল পরে একদিন চলে এলেন। এসেই হৈ রৈ করে বলতে শুরু করলেন, ‘দেখতে আসলাম কেমন আছ (কোনও আপনি টাপনির বালাই নেই।) খবর কি, বল। আমি ত কলকাতা থেকে আসলাম পরশুদিন। জানো তো আমি কলকাতায় গেলে সুনীলের বাড়িতেই থাকি। সুনীল আর স্বাতী তো আমারে অন্য কোথাও থাকতেই দেয় না। সুনীল বলছিল তোমার কথা। তো আমি সুনীলকে বললাম, যাবো দেখি একবার তসলিমার বাসায়। নবনীতার সাথে তোমার আলাপ আছে? নবনীতা দেব সেন! চিনো তো নিশ্চয়ই। আমারে বলছিল তার বাড়িতে যেতে, কিন্তু আর হইল না। তা তোমার খবর কি বল। কবে যাচ্ছ কলকাতায়। ওইখানে তো তোমার নাম বললেই সবাই চেনে। বাদলের কাছ থেকে তোমার একটা বই নিয়া আসার কথা ভাবছিলাম। সময়ই পাই নাই।’ একাই দীর্ঘক্ষণ বকতে পারেন মোস্তফা কামাল। ‘সুনীল তো আমাকে নিয়া একটা বই লিখছে, বইটা পড়ছ? আমি যা যা বলছি সুনীল রেকর্ড কইরা নিছে। তার পর তো পুরা একটা বইই লিইখ্যা ফেলল।’ বকবক বকবক। ‘ফেরদৌসের সাথে ত আমার মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ভাই হইলে কী হইব, আমি কেয়ার করি না।’ বকবক। হঠাৎ হঠাৎ মোস্তফা কামাল আমার বাড়িতে এরকম উদয় হয়ে যতক্ষণ থাকেন মাতিয়ে রাখেন বাড়ি। যেন আমার সঙ্গে তাঁর হাজার বছরের বন্ধুত্ব, যেন আমি তাঁর চারপাশের সবাইকে চিনি, এমন ভাবে বলতে থাকেন তাঁর আত্মীয়রা, পাড়া পড়শিরা, বন্ধুরা কে কী করল, কে কী বলল। নিজের পাঁকে পড়া, পাকে পড়া আর ডুবে যাওয়ার গল্পও অনায়াসে করতে পারেন। ‘ডোরারে বিয়া করলাম, কানাডায় নিয়া গেলাম, পরে ডোরা তো আমারে ছাইড়া চইলা গেল। আমি পোড়া কপাল নিয়া জন্মাইছি বুঝছ! যে ব্যবসাই ধরি, সব ব্যবসায় ফেল মারি। দেখি আরেকটার কথা চিন্তা ভাবনা করতাছি। মালোশিয়ায় চাকরানি সাপ্লাই দিব। এইটার ডিমাণ্ড আছে। .. আমার ত বাড়ি নাই গাড়ি নাই। টাকা পয়সা আজ আছে, কাল নাই। ..আমার ভাইগুলা সব ভাল অবস্থায় আছে, থাকুক। আসলে কি জানো, আমরে কেউ পছন্দ করে না, একটু পাগল পাগল আছি ত তাই।’ তিনি একদিকে গর্ব করছেন যে নামি দামি লোকের সঙ্গে তার খাতির আছে, আবার নিজে যে কিছুই না, নিজে যে একটি ঘোড়ার ডিম সেকথাও দ্বিধাহীন বলে যান। এই মোস্তফা কামালই আমার নিরূপায় অবস্থার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘পাণ্ডুলিপি দিতে চাও, ঠিক আছে আমি নিয়া যাবো।’
‘ঠিক তো!’
‘ঠিক।’
‘কোনও অসুবিধা হবে না তো!’
‘কেন, কী হবে, কে কি করবে?’
ডাক্তার রশীদ ছিলেন পাশে। বললেন এ বাড়িতে যারাই আসে, এ বাড়ি থেকে যারাই বেরোয়, সবার পেছনে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক ঘোরে। লজ্জার পাণ্ডুলিপি হাতে ধরা পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। লজ্জা তো শুধু বিক্রিই নিষিদ্ধ নয়, লজ্জার সংরক্ষণও এ দেশে নিষিদ্ধ। মোস্তফা কামালের মুখটি সাদা হয়ে যায় মুহূর্তে। তিনি পাণ্ডুলিপি কলকাতায় বাদল বসুর হাতে পৌঁছে দেবেন, এ কথা যখন বুক ফুলিয়ে বলেছেন, এটি তিনি ফেলে দেন না, তবে এ বাড়ি থেকে পাণ্ডুলিপি তিনি বেরোবেন না, তাঁকে কাল ভোর ছটায় বিমান বন্দরের রাস্তায় পাণ্ডুলিপি যেন দেওয়া হয়। কে এই দায়িত্ব নেবে! পাণ্ডুলিপি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোবে কে? ডাক্তার রশীদ বললেন, তিনি। কোন রাস্তা, কোন মোড়, কী পোশাক, কী থেকে নামা, ডানে না বামে, কালো ব্রিফকেস, কালো চশমা ইত্যাদি ব্যপার স্যপারগুলো দুজন বসে সেরে নেন। ফিসফিস। দেওয়ালেরও কান আছে। পাণ্ডুলিপি থেকে বইএর নাম লেখকের নাম সব বিদেয় করা হল। রাতের অন্ধকারে ধড়ফড় বুক কম্পমান পা ঘর্মাক্ত গা আর ধুসর পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে রশীদ বেরোলেন, আল্লাহ বিশ্বাস করলে আল্লাহর নাম জপতেন। রাতে ডাক্তার রশীদ পাণ্ডুলিপিখানি তাঁর বালিশের তলে রেখে নির্ঘুম রাত পার করে ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে গেছেন। মহাখালির সাত রাস্তার মোড় পার হয়ে যে বিন্দুতে তাঁর দাঁড়ানোর কথা ছিল সেই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে, কোত্থেকে যাদুমন্ত্রে অনেকটা অন্য গ্রহ থেকে আসা কারও মত কালো চশমার আচম্বিতে উদয় হলে, তাঁর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের ভেতরের বাদামি প্যাকেটটি যেন এক ঠোঙা টোস্ট বিস্কুট নয়ত নতুন শুরু করা কোনও গার্মেন্টসের স্যাম্পল—চলে যায় কালো ব্রিফকেসে। নিঃশব্দে কাঁধে ঝোলা দক্ষিণে যান, কালো চশমা উত্তরে। দুজনের জন্যই অপেক্ষারত দ্রুত যানে অদৃশ্য হয়ে যান দুজন, কারও অনুসরণের শিকার হওয়ার আগেই।
লজ্জা চলে গেল সীমানা পেরিয়ে।
পশ্চিমবঙ্গে ছাপার উদ্দেশে আমি লজ্জা লিখিনি। লজ্জা বাংলাদেশের জন্য। লজ্জা নামে যে একটি বই লিখেছি তা আনন্দ পাবলিশার্সের গোচরে এসেছে ওখানে বাংলাদেশের লজ্জা সংস্করণটি নকল হওয়ার পর। শেষ অবদি পুলিশ লাগিয়ে আনন্দ পাবলিশার্সের কর্মকর্তারা কয়েকজন নকলবাজকে জেলে পুরেছেন। তাঁরা কতটা নীতির কারণে করেছেন, কতটা ব্যবসার কারণে তার খোঁজ নিইনি। মোস্তফা কামালের নিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপিটি কলকাতায় পাঠানো লজ্জার প্রথম পাণ্ডুলিপি। লজ্জা ছাপা হচ্ছে কলকাতায়। নিষিদ্ধ ব্যপারটি বোধহয় সংক্রামক। খবর ছাপা হয়েছে শ্রীলঙ্কায় লজ্জা বইটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওখানে বইটি নিষিদ্ধ করার কী কারণ থাকতে পারে তা আমি জানি না। লজ্জা সম্পর্কে আলোচনার কোনও শেষ নেই। আলোচনা চলছেই। আলোচনা রাস্তা ঘাটে, ট্রেনে বাসে, ঘরে বারান্দায়, আপিসে আদালতে, দোকানে ময়দানে…।
আমার বাড়িতে শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ বেলাল চৌধুরীরা বসে যখন কথা বলছিলেন, কথা গড়াতে গড়াতে লজ্জার দিকে গেল।
‘বিজেপি নাকি লজ্জা ছেপেছে। অনুবাদও করেছে।’ বেলাল চৌধুরী বললেন ইনকিলাব পত্রিকাটি চোখের সামনে মেলে ধরে।
নির্মলেন্দু গুণ বললেন, ‘বিজেপি ছেপেছে বা অনুবাদ করেছে বলে যে মোল্লাগুলো তসলিমার দোষ দিচ্ছে, এটা কি তসলিমার দোষ? আমার কবিতা যদি গোলাম আযমের খুব পছন্দ হয়, সে কি আমার দোষ?’
আমি বলি, ‘বিজেপি পুরো বই অনুবাদ করবে কি করে? বইয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অনেক কথা লেখা আছে। জামাতে ইসলামি আর বিজেপিকে এক কাতারে ফেলা হয়েছে।’
শামসুর রাহমানের মতে লজ্জায় সব ঠিক আছে কেবল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দেশে যে আন্দোলন হয়েছে তার পুরো চিত্রটি নেই, এ দেশে যে অসাম্প্রদায়িক মানুষ আছেন, তা লজ্জা পড়ে বোঝা যায় না। আমি শামসুর রাহমানের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে বলেছি যে আমি একজন ক্ষুব্ধ হিন্দু যুবকের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনা বর্ণনা করতে চেয়েছি, তার চোখে তখন অসাম্প্রদায়িক কোনও কিছু পড়ছে না।
শামসুর রাহমান বিজেপির প্রসঙ্গে বললেন, ‘একটি অসাম্প্রদায়িক বইকে সাম্প্রদায়িক বানানোর চেষ্টা হচ্ছে কি রকম দেখ! কলকাতায় দেবেশ রায় ওখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের পক্ষে উপন্যাস লিখেছেন, সেটি কি এদেশের মুসলমানদের চোখে পড়ে না!’
নির্মলেন্দু গুণ জোরে হেসে উঠে বললেন, ‘মোল্লারা প্রচার করছে, লজ্জা লেখার জন্য তসলিমাকে নাকি পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা দিয়েছে বিজেপি। তা কই? আমাদেরও কিছু ভাগ দাও তসলিমা। একা একা সব টাকা খাবে নাকি!’
আমি হেসে বলি, ‘ইনকিলাবে লেখা হচ্ছে এই টাকার কথা। এখন সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করে যে সত্যি সত্যিই আমাকে বিজেপি টাকা দিয়েছে।’
শামসুর রাহমান বললেন, ‘টাকা দিয়েছে, বলেই খালাশ! প্রমাণ করছে না কেন? নির্বাচনের আগে বিএনপি বলেছিল হাসিনাকে নাকি ভারত পাঁচশ কোটি টাকা দিয়েছে। আওয়ামী লীগও বলেছিল খালেদাকে পাকিস্তান থেকে ছশ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। টাকা নেওয়ার প্রমাণ কেউ কিন্তু এখনও হাজির করতে পারেনি।’
আমি বলি, ‘একই রকম লজ্জা লেখার জন্য আমাকে টাকা দিয়েছে বলে যারা প্রচার করছে, তারা প্রমাণ করতে পারবে না এর সামান্য সত্যতা। কিন্তু প্রশ্ন হল, তারা অপপ্রচার করছে কেন? তারা কি তবে কংগ্রেসের টাকা খেয়েছে? নাকি সিপিএমএর?’
বেলাল চৌধুরী ইনকিলাব পত্রিকাটি ধুত্তুরি বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, ‘লজ্জা লিখে হিন্দুদের যতটা উপকার করেছে তসলিমা, তার চেয়ে বেশি করেছে মুসলমানের উপকার। মুসলমান কত মানবিক হতে পারে তার একটি উদাহরণ লজ্জা। মেজরিটি কমিউনিটি থেকে মাইনরিটির পক্ষে কথা বলা, তাও আবার এমন জোরে সোরে, সে খুব একটা দেখা যায় না। মুসলমানরা এটি সময় সুযোগ পেলে কাজে লাগাতে পারে, বলবে, দেখ দেখ, মুসলমান কত উদার হতে পারে।’
আমি হেসে উঠি, ‘বেলাল ভাই, নাস্তিক মানুষটিকে খুব যে মুসলমান বানিয়ে ফেলছেন।’
‘নাস্তিক তো আমরা সবাই। কিন্তু যেহেতু মুসলমান নাম ধারণ করছ, তাই মুসলমানের গোত্রেই তোমাকে ফেলবে। এখানে নাস্তিক বলে কাউকে তো ধরা হয় না। হয় তুমি মুসলমান, হয় তুমি হিন্দু। নয় বৌদ্ধ, নয় খ্রিস্টান। যেন ধর্ম থাকতেই হবে।’
‘অশিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতি হচ্ছে ধর্ম আর শিক্ষিত মানুষের ধর্ম হচ্ছে সংষ্কৃতি। কি বলেন রাহমান ভাই! ঠিক না!’ তাকাই শামসুর রাহমানের দিকে।
শামসুর রাহমান বললেন, ‘শিক্ষিত কারা? গোলাম আযমও তো শিক্ষিত, ফরহাদ মজহারও শিক্ষিত। দুজনেরই ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি আছে।’
‘না, না, একাডেমিক শিক্ষার কথা বলছি না। কোনও দিন ইশকুল কলেজে যায়নি, এমন মানুষও তো শিক্ষিত হতে পারে। আরজ আলী মাতব্বুরের কথাই ধরুন না।’
বেলাল চৌধুরী উত্তেজিত আরজ আলীর প্রসঙ্গে। ‘আরজ আলী গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক। অথচ কী আশ্চর্য সুন্দর বই লিখেছেন তিনি। তাঁর বই ইশকুলের পাঠ্য হওয়া উচিত।’
শামসুর রাহমান সায় দিলেন, আরও খানিকটা যোগ করে, ‘কেবল ইশকুলেই নয়, কলেজ ইউনিভার্সিটির সিলেবাসেও থাকা উচিত। এ বই পড়লে ধর্ম সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে। অনেককেই নাস্তিক হওয়ার প্রেরণা পাবে।’
ট্রেতে চা দিয়ে যায় কুলসুম। সকলের হাতে চায়ের কাপ। এর মধ্যে নিঃশব্দে ডাক্তার রশীদ এসে আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তার রশীদ এককালে জাসদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন, এখন অক্রিয়। সাম্প্রদায়িকতা ধর্মান্ধতা কুসংস্কার এসবের প্রচণ্ড বিরোধী। চিন্তা ভাবনা তুখোড়। চায়ে চুমুক দিয়ে একটি প্রশ্ন আমার মনে উঁকি দেয়, মুসলমানরা যদি সব নাস্তিক হয়ে যায়, তবে কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! আমার মন বলে, হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গোলাম আযম একজন নাস্তিক। জামাতের সবগুলো নেতাকেই আমার নাস্তিক মনে হয়, আস্তিক হল তারা যারা গোলাম আযমের অনুসারী, বোকা, বুদ্ধু। যাদের নাকে ধর্মের রশি লাগিয়ে গোলাম আযম রাজনীতির খেলা দেখাচ্ছেন। আমি চা রেখে শামসুর রাহমানকে বলি, ‘আমার কিন্তু মনে হয় গোলাম আযম একজন নাস্তিক। এরশাদের কথাই ধরেন, এরশাদ কি ধর্ম মানত নাকি? এই যে হুট করে সংবিধান পাল্টো রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করে দিল, এটা কি ইসলামের প্রতি ভালবাসায় করেছে? মোটেই তো তা নয়। ক্ষমতার লোভে ধর্মকে ব্যবহার করেছে।’
‘হ্যাঁ পলিটিক্যাল ইসলাম তো এরকমই। আমারও বিশ্বাস ধর্মকে যারা রাজনীতিতে ব্যবহার করে, তারা খুব ভাল করেই জানে ধর্ম হচ্ছে মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখার আর মুর্খ বানিয়ে রাখার অস্ত্র। অস্ত্রটি যারা ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে, তারা আসলে আদৌ ধর্মে বিশ্বাস করে কি না সন্দেহ আছে।’
‘ধরেন যদি করেই বিশ্বাস, তারপরও কিন্তু তারা ইসলামের আদর্শই মানছে। কারণ ইসলামে আছে পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত, একটি হচ্ছে দারুল ইসলাম আরেকটি দারুল হারব। দারুল হারব মানে বিধর্মীদের অঞ্চল, দারুল ইসলাম মানে ইসলামের অঞ্চল। মুসলমানের কাজ হল দারুল হারবের বাড়িঘর ভেঙে চুড়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অমুসলমানদের যেমন করে সম্ভব মুসলমান বানিয়ে, অথবা সম্ভব না হলে ওদের খুন করে দারুল হারবকে দারুল ইসলাম বানানো। তার মানে টার্ণেট হচ্ছে পুরো পৃথিবীটাকে দারুল ইসলাম বানানো। তাহলে বাংলাদেশে মুসলমানরা যা করছে, এ তো কোনও ইসলামনীতিবিরুদ্ধ কাজ নয়। ইসলাম তো এ কাজটি সমর্থনই করে।’
‘এ তো কেবল ইসলামের নীতি নয়। খ্রিস্টানদেরও তো ও একই নীতি ছিল, তা না হলে ওই ধর্ম কোথায় শুরু হয়েছিল, আর কতদূর বিস্তৃত হয়েছে, দেখ।’
‘তা ঠিক। একেশ্বরবাদগুলোর অতীত ইতিহাস বড় জঘন্য। কিন্তু রাহমান ভাই, এখনও কেন? এই বিংশ শতাব্দির শেষে এসে এখনও কেন দেখতে হচ্ছে মধ্য যুগের সেই নির্মমতা!’
‘মানুষ এখনো মানুষ হয়নি বলে!’
‘কিন্তু ক্রিশ্চানদের মধ্যে তো বিধর্মীকে মেরে ফেলো, এই ব্যপারগুলো আর নেই। মুসলমানদের মধ্যে রয়ে গেছে কেন!’
‘কারণ মুসলমান রাষ্ট্রগুলো সেভাবে সেকুলার হয়নি, যেভাবে ক্রিশ্চানদের দেশগুলো হয়েছে।’
‘কিন্তু মুভমেন্ট তো ছিল। প্যান আরব মুভমেন্টএর কথাই ধরেন। এ তো সেকুলার দলের আন্দোলন। এর মধ্যে প্রায় সবাই তো আরবদেশগুলোর মুসলমান।’
‘আরব দেশের সেকুলার মুভমেন্ট নষ্ট হওয়ার পেছনে কিছু কিছু বদ আরব নেতার অবদান আছে, অবশ্য তারাও ঔপনিবেশিক শক্তির চক্রান্তের শিকার। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো বড় কোনও মুভমেন্ট তাদের কলোনিগুলোতে বরদাস্ত করেনি, বিশেষ করে যে মুভমেন্ট ওই শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে।’
‘কিন্তু রাহমান ভাই, প্যান আরব মুভমেন্ট তো কলোনিয়লিস্টরা চলে যাওয়ার পর হয়েছে।’
ডাক্তার রশীদ বললেন, ‘ইমপেরিয়ালিস্টরা আর কতদূর গেছে! তেলের লোভে যে করেই হোক থেকে গেছে মিডল ইস্টে। তেল কারা কন্ট্রোল করেছে? সে তো ব্রিটিশই। পরে আমেরিকা ব্রিটিশের ভূমিকা নিল। প্যান ন্যাশনালিজমের নেতারা তেলের ইন্ডাস্ট্রি ন্যাশনালাইজ করার জন্য কম আন্দোলন করেছে!..’
‘ইসলামিক ব্রাদার হুড এই জাতীয় মৌলবাদী আন্দোলনও তো গড়ে উঠল ইমপেরিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে। এদেরও একটা ভুমিকা আছে সেকুলার আন্দোলন নষ্ট করার।’ আমি বলি।
‘আরব নেতাগুলোর পরষ্পরের প্রতি বিরোধ থাকার কারণেই তারা এক হতে পারেনি। মিশরের নাসের চেয়েছিল সব আরবদেশগুলোকে এক করে ফেলতে। কিন্তু অন্য ন্যাশনালিস্টরা আবার তা চায়নি। আজ আরব দেশগুলোর মধ্যে যদি ইউনিটি থাকত, তবে কোনও আমেরিকান বা ব্রিটিশের ক্ষমতা থাকত না ওখানে কোনও পাপেট বসিয়ে কলকাঠি নাড়ার।’ ডাক্তার রশীদ মন্তব্য করেন। তিনি উত্তেজিত। ঢক ঢক করে ঠাণ্ডা চা গিললেন।
‘এখন যে ইসলামি মৌলবাদ বাড়ছে মধ্যপ্রাচ্যে, এর কারণ কি আরব মুল্লুকে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইজরাইলি সন্ত্রাস? নাকি বার্লিন ওয়াল? বার্লিন ওয়াল ভেঙে গেছে, ধর্মহীন সোভিয়েতের পতন হয়েছে, এর মানে ধর্মহীনতার পতন হয়েছে। সুতরাং হে ধর্ম জেগে ওঠো। ওহে ইসলাম ..।’
বেলাল চৌধুরী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ইণ্ডিয়ান সাবকণ্টিনেণ্টের ইতিহাস আলাদা, এখানে মৌলবাদ শক্তিশালী হওয়ার পেছনে সরকারি মদদটাই বেশি।’
‘তা তো অবশ্যই। কিন্তু মৌলবাদ সংক্রামকও বটে। এক জায়গায় বাড়লে আরেক জায়গায় বাড়ে। …’
শামসুর রাহমান রাগী মুখে বললেন, ‘বাংলাদেশের হারামজাদা জামাতিগুলো পাকিস্তানের দিকে মুখ করে.. .’
হঠাৎ দরজায় শব্দ হয়। শামসুর রাহমান তাঁর অসম্পূর্ণ বাক্যটি শেষ না করেই দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ডাক্তার রশীদ উঠে গেলেন দরজায়। আমাদের চোখ নাক কান দরজায়। কোনও অচেনা আগন্তুকের এ বাড়িতে ঢোকা উচিত নয়, এ কথা সকলে জানেন। প্রতি শুক্রবারে মসজিদের খুতবায় আমার বিরুদ্ধে গালিগালাজ চলছে। তসলিমার ফাঁসি চাই বলে মিছিল বেরোচ্ছে। এ সময়, যে কোনও ধর্মপ্রাণ মুসলমান আমার বাড়িতে ঢুকে আমাকে নির্মম কোনও আশীর্বাদ করতে পারেন। সে রকম কেউ দরজায় কি? তা না হলে রশীদ কেন ঢুকতে দিচ্ছেন না আগন্তুককে! দরজা আগলে দাঁড়িয়ে তিনি কথা বলছেন আগন্তুকের সঙ্গে। কিছুক্ষণ কথা বলে দরজা খোলা রেখেই রশীদ দু পা এগিয়ে এলেন আমার দিকে, বললেন, ‘শনির আখড়া থেকে চারটে ছেলে এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।’
‘কি নাম? কেন এসেছে?’
‘তুমি চিনবে না, একজনের নাম শংকর রায়।’
গুণ বলে উঠলেন, ‘ঢুকতে দেবেন না। দরজা বন্ধ করে দেন। কে না কে হিন্দু নাম নিয়ে এখানে অন্য মতলবে এসেছে হয়ত।’ বলে আবার হেসে উঠলেন বলতে বলতে, ‘হিন্দুদেরই বা বিশ্বাস কি?’
রশীদ এবারও দু পা ফিরে গিয়ে ওদের সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে কী কথা বলে নিয়ে আমাকে বললেন, ‘শোনো, এরা খুব সাধারণ মানুষ। একবার তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে। করেই চলে যাবে।’
আমি প্রণামের লোভে নয়, কেন এসেছে, কে তারা, এই উৎসাহেই, অথবা এতগুলো মানুষ এখানে বসে আছে, কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে এরা ঠেকাবেন এই সাহসেই বললাম, ‘ঠিক আছে, আসতে বলেন।’
চার যুবক ঢুকল ঘরে। কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স। সাদাসিধে কাপড় পরনে, স্যাণ্ডেল পায়ে। দরজার কাছে স্যাণ্ডেলগুলো খুলে চারদিক একবার দেখে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে হাত বাড়ালো আমার পায়ের দিকে। আমি দ্রুত পা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কোনও প্রশ্ন করার আগেই শংকর নামের ছেলেটি করজোড়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘দিদি, আপনি আমাদের দেবী। আপনাকে দেখতে পেয়ে জীবন আমাদের সার্থক হল। অনেক কষ্ট করে আপনাকে খুঁজে পেয়েছি, দিদি। আপনাকে একবার প্রণাম করতে দেন।’ পা ছুঁতে গেলে আবার আমি সরিয়ে নিই পা। শংকর তিনজনের মধ্যে দুজনকে দেখিয়ে বলে, ‘এরা দুজন আমার কাজিন,’ বাকি লাল শার্ট পরা একজনকে দেখিয়ে, ঞ্চআর এ হল আমার বন্ধু। আমরা কলেজে পড়ি দিদি।’
আবারও মাথা আমার আমার পায়ের দিকে নাবাতেই বলি, ‘না না প্রণাম করতে হবে না। আমি এসব পছন্দ করি না। কিছু বলার থাকলে বলেন।’
‘দিদি, আপনার লজ্জা বইটা আমরা পড়েছি দিদি। আমাদের কথা আগে কেউ এমন করে বলে নাই দিদি। দিদি আপনি যা করেছেন, তা যে কত বড়.. আমাদের মনের কথাটা আপনি লিখেছেন।’
‘শোনেন, হিন্দু মুসলমান এখানে বড় ব্যপার না। আমি মানষ হয়ে মানুষের কষ্টের কথা বলেছি। এই যে এখানে দেখছেন যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা সবাই লেখেন, সবাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন।’
‘দিদি আমার কাজিনদের বাড়ি ভেঙে ফেলেছে জামাতিরা। আর আমার এই বন্ধু, সমীরণ, সমীরণের এক ভাইকে খুন করেছে ওরা।’
বলতে বলতে চার যুবক আমি বাধা দেওয়ার পরও আমার পা জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। মহা সমস্যায় পড়ি। না পারছি ওদের টেনে তুলতে, না পারছি পা সরাতে। এক শরীর অস্বস্তি নিয়ে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকি।
কেঁদে, চোখ মুছে, শংকর তার ভাই বন্ধু সহ বিদায় হল।
ওরা চলে গেলে নির্মলেন্দু গুণ খুব ধীরে খুব গাঢ় স্বরে বললেন, ‘লজ্জা লিখে আসলে তসলিমা বাংলাদেশের হিন্দুদের অপকার করেছে, উপকার নয়।’
‘মানে?’ আমার বিস্মিত চোখ গুণের নির্বিকার মুখে।
আর সকলের চোখেও দেখি একই রকম বিস্ময়।
‘অপকারটা কিরকম শুনি!’ আমি উদগ্রীব শুনতে।
গুণ খুব ধীরে ধীরে বললেন, ‘হিন্দুদের মনে যে তীব্র আগুন জ্বলছিল, সেটিকে তসলিমা নিভিয়ে দিয়েছে। যে ক্ষোভ তাদের জমা ছিল বুকে, যে ক্ষোভের কারণে তারা ভয়ংকর কিছু করতে পারত, সেটিকে কমিয়ে দিয়েছে। তারা এখন ভাবতে পারছে তাদের পক্ষ হয়ে লড়বার মানুষ আছে, তারা একা নয়। দুর্বলের পাশে সবলের পক্ষ থেকে কেউ দাঁড়ালে দুর্বল কিন্তু দমে আসে। তারা যে আগুন লাগাতে চায়, সে আগুন তারা আর লাগায় না।’
আমরা আমাদের শূন্য চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসে থাকি। অনেকক্ষণ একটি বিষণ্ন নিস্তব্ধতা আমাদের দখল করে রাখে।
শান্তিবাগের বাড়িতে এরপর খুব বেশিদিন থাকা সম্ভব হয় না। কারণ বাড়িঅলা আমার দিকে অন্যরকম চোখে তাকাতে শুরু করেছেন। পাঁচবেলা নামাজ পড়া লোক বাড়িঅলা, বাড়িতে ইনকিলাব পত্রিকা রাখেন। জুম্মাহর নামাজ পড়তে মসজিদে যান, যে মসজিদে নামাজের পর ইমাম খুৎবা পড়েন, খুৎবা না তো, মিলন বলেন, আপনের গিবৎ পড়ে। মিলনও মাঝে মাঝে শুক্রবারে শান্তিবাগের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে আসে আর শুনে আসে ইমামের গালি। ‘তসলিমা নামে এক কুলাঙ্গার জন্ম নিয়েছে এদেশে, ভাইয়েরা আমার, এই তসলিমা ইসলামবিদ্বেষী, মুসলমান হয়ে মুসলমানের সর্বনাশ করছে। হিন্দুদের ঘুষ খেয়ে এই পাপীনি একটা বই লিখেছে। বই টা আপনারা যদি না পড়ে থাকেন, ভাল কাজ করেছেন, সওয়াবের কাজ করেছেন। ওই বইএ লিখেছে মুসলমান জাতি নাকি জঘন্য জাতি। মুসলমান নাকি হিন্দুদের খুন করে রাস্তা ঘাট ভাসিয়ে দিয়েছে রক্তের বন্যায়। এই মহিলা নারীজাতির লজ্জা। নারীজাতিকে প্ররোচনা দিচ্ছে পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেলা করতে। স্বামীদেরে ত্যাগ করতে। এই মহিলা ধর্ম বিশ্বাস করে না। বলে আল্লাহ বলতে কিছু নাই। বলে, মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইসসালাম, আল্লাহর পেয়ারা নবী, তিনি নাকি কামুক, তিনি নাকি বদমাইশ লোক। তওবা তওবা। ভাইয়েরা আমার, সরকারের কাছে দাবি করেন, এই কুলাঙ্গার পাপীনির যেন একটা বই না, যতগুলা বই সে লিখেছে, সব যেন আগুনে পোড়ায়, সব যেন নিষিদ্ধ করে। তার ফাঁসির দাবি করেন। এই পাপীনির ফাঁসি হলে এই দেশ বাঁচবে, ইসলাম বাঁচবে।’
আল্লাহর কাছে দুহাত তুলে মোনাজাত হয়, মোনাজাতে তসলিমার ফাঁসি দিয়ে দেশ ও মুসলমান জাতিকে রক্ষা করার অনুরোধ জানানো হয়। কোনও কোনওদিন লিফলেট বিলি হয় এসব কথার। এ সবও শোনেন বাড়িঅলা। রাস্তায় মিছিল বেরোয় তার ভাড়াটের ফাঁসির দাবিতে, তাও তিনি দেখেন, না দেখলেও পত্রিকায় পড়েন। হাসপাতালে যাওয়ার পথে আমি নিজেই দুদিন পড়েছি মিছিলের সামনে। একদিন পাশ কাটিয়ে অন্য রাস্তায় চলে গেছি। আরেকদিন সে সুযোগ পাইনি। রিক্সা থেমে আছে, রাস্তায় বিশাল মিছিল যাচ্ছে। আমার রিক্সার পাশ দিয়েই চলে যাচ্ছে টুপিঅলারা চিৎকার করতে করতে তসলিমার ফাঁসি চাই, দিতে হবে। আমার ওড়না নেই যে ওড়নায় মুখ লুকোনো। জামা পাজামার ওপর এপ্রোন পরা। আমি প্রাণ হাতে নিয়ে বসে থাকি রিক্সায়। যেন ধুলো এড়াতে নাক মুখ ঢাকছি, এভাবে হাত দিয়ে ঢেকে রাখি মুখের অর্ধাংশ, চোখ নামিয়ে রাখি রিক্সার পাদানিতে। যেন লজ্জাশীলা মেয়েমানুষ আমি পর পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকাই না। মিছিলের কেউ একজন যদি আমাকে চিনে ফেলে, সে যদি চেঁচিয়ে তার সগোত্রীয়দের জানিয়ে দেয় যে আমাকে হাতে নাতে পাওয়া গেছে, তখন আমার ছিন্নভিন্ন অস্থি মজ্জা মাংস এই রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে, সে ব্যপারে আমার কোনও সন্দেহ থাকে না। মিছিল শেষ হলে রিক্সাঅলা যখন চালাতে শুরু করে, খানিকটা পথ গেলে আমি জিজ্ঞেস করি, কিসের মিছিল গেল?
তসলিমার মিছিল।
তসলিমার মিছিল মানে?
তসলিমার ফাঁসি চাইতাছে লোকেরা।
কেন ফাঁসি চায়? তসলিমা কি করছে?
তসলিমা মসজিদ ভাইঙ্গা দিছে।
কোন মসজিদ, জানেন?
বাবরি মসজিদ।
একটা মেয়েমানুষ কি কইরা একটা মসজিদ ভাঙল?
তা জানিনা কি কইরা ভাঙছে।
কোথায় শুনলেন এই সব।
আমরা শুনি। দেলোয়ার হোসেন সাইদির ক্যাসেট বাজে রাস্তাঘাটে। মিছিল দেখছি।
আপনিও চান তসলিমার ফাঁসি।
হ। চামু না কেন? সবাই যখন চায়, আমিও চাই।
শান্তিবাগে বাড়ির গেটের কাছে থেমে রিক্সাভাড়া মিটিয়ে দিই। ভাল যে গেটে ঝোলানো সাইনবোর্ডটি আগেই তুলে নিয়েছি।
যেদিন মিছিলের সামনে পড়ি, সেদিনই ছোটদা আসেন তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার খুব ভাল লাগে ছোটদাকে দেখে। ছোটদা সাধারণত আমার বাড়িতে আসেন না। তাঁর বাড়িতে গীতার দুর্ব্যবহার সইতে আর সুহৃদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার দেখতে যেতে ইচ্ছে করে না বলে যাই না। ছোটদা যে বন্ধুটি নিয়ে আমার বাড়িতে আসেন, তাঁর নাম শফিক। তিনি ছোটদার সঙ্গেই বিমানে চাকরি করেন। তিনি একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছেন আমার কাছে। অনুরোধটি হল বিমানবালাদের যে পঁয়ত্রিশ বছর পর চাকরি থেকে বিদায় দিয়ে দেওয়া হয়, তারা যে গর্ভবতী হওয়ার পর ন মাস ছুটি পাওয়ার কথা, তা পায় না, এবং কোনও কোনও পেনশন থেকেও বঞ্চিত হয় সে বিষয়ে আমি যেন কিছু লিখি। কথায় কথায় যখন ছোটদা জানালেন যে শফিক গাড়ির ব্যবসা করে, জাপান থেকে ব্যবহৃত গাড়ি এনে এখানে বিক্রি করে, আমি বললাম, আমি কিনব গাড়ি। আজই। তুই চাইলে তো তরে শফিক অনেক কম টাকায় দিতে পারব। তবে আগে কিছু টাকা দিতে হইব। ঠিক হল, আজই আমি কিছু আগাম টাকা দিয়ে দেব, গাড়ি এসে যাবে দু সপ্তাহের মধ্যে। গুণে গুণে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিই। বাকি তিন লক্ষ টাকা দেব গাড়ি পাওয়ার পর। টাকাটা কাকলী পাবলিশার্সের মালিক সেলিম আগের দিন দিয়ে গেছেন বইয়ের অগ্রিম, যে বই এখনও লেখা হয়নি, এখনও ভাবা হয়নি, সে বইয়ের অগ্রিম। সেটাকা নিয়ে শফিক চলে গেলেন। গাড়ি ছাড়া আমার চলাফেরা যে নিরাপদ নয়, সে আমি নিশ্চিত। তাই এই ব্যবস্থা। বিমানবালাদের নিয়ে আমার লেখা ঠিকই হয়, যায় যায় দিন পত্রিকায় তা ছাপাও হয়। কিন্তুৃ সেই গাড়িটি আমার কখনও পাওয়া হয় না এবং সেই টাকাটিও আমাকে আর ফেরত দেওয়া হয় না। বাড়ি থেকে বেরোনোই মানে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বেরোনো। কিন্তু বাড়িতে বসে থাকলে তো আমার চলবে না। আমাকে বেরোতেই হবে। বাড়ির বাইরে যেমন অসন্তোষ বাড়ছে, বাড়ির ভেতরেও তেমন। বাড়িঅলা যে আমাকে তাড়ানোর জন্য মনস্থির করে ফেলেছেন তা আমি টের পাই। বাড়িঅলা এবং তাঁর স্ত্রীর ভ্রূকুঞ্চন, তাঁদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, আমাকে দেখেও না দেখে চলে যাওয়া আমাকে বুঝিয়ে দেয় তাঁরা আমার সঙ্গে আর খাতির জমাতে চাইছেন না। বুঝি তাঁরা আশঙ্কা করছেন যে কোনও একটি মিছিল যে কোনও একদিন এ বাড়ির দিকেই আসবে এবং বাড়িটির ওপর পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেবে মিছিলের লোকেরা। এই ঝুঁকিটি যে বাড়িঅলা নিতে চান না, তা আমি অনুভব করি সকাল বিকাল। দুশ্চিন্তায় ছটফট করি। বাড়িঅলা আজ আমাকে তাড়িয়ে দিলে আমি যাবো কোথায়! কোনও আশ্রয় নেই আমার। কোথাও কোনও নিরাপত্তা নেই। নিশ্চয়তা নেই। আমাকে কোনও বাড়িঅলাই বাড়িভাড়া দেবে না। আমার এই নামটি এখন ভয়ংকর একটি নাম। ভদ্রলোকেরা নাম শুনে আঁতকে ওঠেন। ইশকুল কলেজের যে মেয়েরা ছেলেদের ধমক দিয়ে কথা বলে, মাথা উঁচু করে গট গট করে হাঁটে, বেহায়া বেপরোয়া, তাদের তসলিমা বলে ডেকে টিটকিরি দেওয়া হয়। আমি বুঝে ওঠার আগেই তসলিমা নামটি সাধারণের সমাজে একটি পাপের কলঙ্কের ব্যাভিচারের স্বেচ্ছাচারিতার অনৈতিকতার বিপথগামিতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। শান্তিবাগের রাস্তা ছেড়ে মালিবাগ পাড় হয়ে শান্তিনগরের মোড়ে যে দশ তলা দালান উঠছে ইস্টার্ন হাউজিংএর, সেদিকে যেদিন চোখ পড়ে, সেদিনই বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইস্টার্ন হাউজিং এসটেটের মতিঝিল আপিসে গিয়ে বাড়ি না দেখে, কারও সঙ্গে না বুঝে, কত দাম এত দাম, কোনটা তৈরি আছে, ন তলা, এক নম্বর বিল্ডিং, কত দিতে হবে এখন, এত দিতে হবে, এই নিন চেক, এই নিন বাড়ির দলিল করে একটি বাড়ি কিনে ফেলি। ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ধার নিতে হল, সে ব্যবস্থা ওরাই করে দিল, বাকি কিছু টাকা শোধ করতে হবে কিস্তিতে। বাড়ি কিনলে বাড়ির মালিকরা জিজ্ঞেস করে না আমি কাকে নিয়ে থাকব, আমার স্বামী আছে কি না। জানতে চায় না আমি করি কি, খবর নেয় না আমার নামে মিছিল বেরোচ্ছে কি না। ওরা কেবল দেখতে চায় আমার টাকা আছে কি না বাড়ি কেনার, টাকা থাকলে আমার স্বামীহীন জীবন, আমার লেখালেখি, আমার বিরুদ্ধে কুৎসা গিবৎ, আমার বই বাজেয়াপ্ত, আমার বিরুদ্ধে ফাঁসির মিছিল নিয়ে ভাবে না। বাড়ি কেনা ছাড়া আমার উপায় কিছু ছিল না। প্রকাশকদের দিয়ে যাওয়া টাকা, যা ভেবেছিলাম ব্যাংকে রেখে ইন্টারেস্ট যা পাবো মাসে মাসে, তা দিয়ে সংসারের খরচ চালাবো, চাকরির টাকা আর কত! সেই নিরাপত্তা নির্বাসনে দিয়ে যা টাকা দিয়েছেন প্রকাশকরা আর যা ছিল জমা, সব ঝেড়ে ঝুড়ে দিয়ে আমার বাড়ি কেনা হল। বাড়ির দাম সাতাশ লক্ষ টাকা। বারো লক্ষ টাকা নগদ দেওয়া হল। ব্যংকের ঋণ যত দেরিতে শোধ করব, তত দিতে হবে সুদ। বাড়ি কেনার খবর পেয়ে প্রকাশকরা হুড়মুড় করে আরও অগ্রিম রয়্যালটি ঢালতে শুরু করলেন। কাকলী প্রকাশনী তিন লক্ষ টাকা দিয়ে গেছেন খবর পেয়ে পার্ল পাবলিকেশন্সএর মিনু পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে এলেন। ব্যাংকের টাকা খুব দেরি হয়নি শোধ করতে। এক লক্ষ টাকার জন্য বাবার কাছে হাত পাততে হয়েছিল। অবশ্য ধার হিসেবে নিয়েছি। তিনি দিয়েছেন। জমি কেনা বাড়ি কেনা বিষয়ে বাবা বরাবরই খুব উৎসাহী। দলিল পাওয়ার পরই ঠেলাগাড়ি ডেকে এনে শান্তিবাগ থেকে শান্তিনগরে জিনিসপত্র উঠিয়ে নিলাম। আমার কষ্ট হচ্ছিল শান্তিবাগের বাড়িটি ছেড়ে যেতে। স্মৃতিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সর্বত্র। আমি আর আমার দীর্ঘশ্বাস কালো গেটটি পেরিয়ে যাই।
লজ্জা নিয়ে হৈ চৈ মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে, কমছে না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মাঝমাঠে গিয়ে পড়েছে লজ্জা। লেখালেখি হচ্ছে, বাম দলের লোকেরা বলছে, এ একটা বাজে বই। এমন কী বামপন্থী চিত্রপরিচালক মৃণাল সেন বললেন, লজ্জাকে বই না বলে দুর্গন্ধ-আবর্জনা বলা ভাল। আবার চরমপন্থী হিন্দুরা বলছে এ হচ্ছে পবিত্র গ্রন্থের মত। বাংলাদেশের চিত্রের ঠিক উল্টো চিত্র ভারতে। এদেশে বামপন্থী উদারপন্থী সেকুলারিস্টরা বলছেন, এটি একটি মূল্যবান বই (অবশ্য বদরুদ্দিন ওমর ছাড়া)। ওদিকের একই মানসিকতার মানুষ বলছেন এটি আবর্জনা ছাড়া কিছুই নহে। পশ্চিমবঙ্গের খুব অল্প কিছু মানুষ, হাতে গোণা, বাম ঘেষাঁ হয়েও বইয়ের পক্ষে বলছেন। একটি উপন্যাস কী করে রাজনীতির গুটি হয়ে যায়, আমাকে সবিস্ময়ে তা দেখতে হল। কিন্তু ভাল যে আমাকে আরও কাছ থেকে তা দেখতে হচ্ছে না। কিন্তু আচমকা একদিন কলকাতার আজকাল পত্রিকা থেকে বাহারউদ্দিন এসে উপস্থিত। বাহারউদ্দিনের আগের সেই গদগদ ভঙ্গিটি, সেই গলে যাচ্ছি গলে যাচ্ছি হাসিটি নেই। বরং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার আপদমস্তককে এমন হানে যে মনে হয় এ বুঝি বায়তুল মোকররম মসজিদ থেকে গোলাম আযমের সাক্ষাৎ পুত্রটি এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। আজকাল পত্রিকাটি বামপন্থীর পত্রিকা। আমি আনন্দপুরষ্কার পাওয়ার পর আজকাল আমাকে নিয়ে প্রশংসায় মেতেছিল। বুঝি, মুসলমান মেয়ে বলেই মেতেছিল। আর যেই না দেখল মুসলমান মেয়েটি মুসলমানদের গাল দিয়ে একটি বই লিখেছে, তখনই বেজার হয়ে গেল আজকাল। তবে তো এখন আর আমার গুণ গাওয়া চলবে না। গুণ গাওয়া বাদ দিয়ে বরং তসলিমাকে যত পারে ছি ছি দিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে লজ্জা যখন বিজেপির লোকেরা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। বাহারউদ্দিন এসেছেন আমার কাছে জবাব চাইতে, কেন আমি লজ্জা লিখেছি। বাহারউদ্দিন আসামের লোক, ওখানের এক কলেজে আরবির শিক্ষক ছিলেন। একসময় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে স্বাতী নামের এক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে লালন নামের একটি পুত্রের জন্ম দিয়ে সুখের অথবা অসুখের সংসার করছেন। নিজে তিনি গদ্য পদ্য রচনা করেন। বইও বেরিয়েছে কিছু। বলতে দ্বিধা নেই যে বাহারউদ্দিন বেশ চমৎকার গদ্য লেখেন। তিনি ধর্ম মানেন না। ধর্মকে মুখে বেশ আচ্ছ! করে গাল দেন। ধর্ম নিয়ে যারা মাতম করে, তাদেরও। ওখানে হিন্দুদের অবহেলা অবজ্ঞা পাওয়া সংখ্যালঘু মুসলমানের জন্য আবার মায়া আছে তাঁর। আমার সঙ্গে তাঁর বিরোধ থাকার কথা নয়। কিন্তু বিরোধ সৃষ্টি হয়, যখন দেখেন হিন্দু ধর্মবাদী দল আমাকে দেবী করে তুলছে এবং এ কারণে দোষটি তিনি আমাকে দেন। যে কথাটি বাহারের বোঝা সম্ভব হয় না, তা হল, আমি কোন দেশে বসে কাদের কথা লিখেছি, এবং কেন লিখেছি। বাহারউদ্দিন যত বামপন্থী হন, যত নাস্তিক হন, তিনি সংখ্যালঘুদের একজন। তিনি অত্যাচারী হিন্দু দেখেছেন, অত্যাচারিত হিন্দু দেখেননি। যা দেখে অভ্যেস নেই, তার চিত্র কল্পনা করা সবার জন্য সহজ হয় না। তিনি কলকাতা থেকে উড়ে এসেছেন বলে এই করুণায় নয়, লজ্জা নিয়ে ভুল ভাবনাগুলো শুধরে দেওয়ার জন্য বাহারের সঙ্গে আমি কথা বলতে রাজি হই। আজকাল পত্রিকায় লজ্জা নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছে। বাদ প্রতিবাদ তুঙ্গে। মুসলমান মৌলবাদিরা নয়, প্রগতিশীল শিবিরের এমনকী স্বনামধন্য বামপন্থী লেখক এবং নেতারা মন্তব্য করেছেন, ক. আমি উস্কানিমূলক লেখা লিখেছি। খ. আমি সচেতন বা অসচেতনভাবে বিজেপি- আরএসএস মার্কা হিন্দু মৌলবাদের স্রোতে ভেসেছি। এমনকী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে যে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত তার শিকার হয়েছি। গ. উপন্যাস হিসেবে লজ্জা দুর্বল। পলায়নবাদী দৃষ্টিকোণে সমগ্র রচনাটি আচ্ছন্ন।
বাহার আমাকে প্রশ্ন করেন, ‘লজ্জা নিয়ে আপনি তো নিশ্চয়ই এখন বিব্রত। তাই না?’
কপালে আমার বিরক্তির ভাঁজ পড়ে প্রথম প্রশ্নটি শুনেই।
‘আশ্চর্য তো! কেন বিব্রত হব। মোটেও আমি বিব্রত নই।’
‘লজ্জা কিংবা আপনার কোনও লেখা নিয়েই কি আপনি বিব্রত নন, বলতে চান?’
‘হ্যাঁ বলতে চাই। আমার লেখার বিষয় নিয়ে আমি কখনও বিব্রত হই না। আমার দুর্বল বর্ণনা নিয়ে, ভাষা ব্যবহারের অপরিপককতা নিয়ে, চরিত্রের গভীরে যথেষ্ট না পৌঁছোনো নিয়ে অবশ্য বিব্রত হই।’
‘লজ্জাকে বাংলাদেশে ইসু করেছে মোল্লারা, সরকারও। পশ্চিম বাংলায় এবং ভারতের আরও অন্যান্য রাজ্যগুলোয় আপনার অসতর্কতার ফায়দা তুলেছে বিজেপি। আপনার কি মনে হয় না সংঘ পরিবারের হাতে আপনি বিপজ্জনক অস্ত্রটি তুলে দিয়েছেন?’
‘প্রথমেই আপনার অসতর্ক শব্দ নিয়ে আমি আপত্তি করছি। লজ্জা লিখবার সময় আমি মোটেও অসতর্ক ছিলাম না। লজ্জায় আমি স্বীকার করছি কাঠামোগত দুর্বলতা, শিল্পগুণের অভাব প্রচুর আছে কিন্তু লজ্জার বিষয় বা বক্তব্যে কোনও ত্রুটি নেই। আমি অকপটে সত্য কথা লিখেছি। বাংলাদেশ সরকার লজ্জা নিষিদ্ধ করতে গিয়ে একবারও কিন্তু বলেনি বইয়ের কোনও তথ্য ভুল। বিজিপি যদি ফায়দা তোলে সেটি বিজিপির অসততা, সেটি নিশ্চয়ই লজ্জার কোনও ত্রুটি নয়। সঙ্ঘ পরিবারের হাতে আমি অস্ত্র তুলে দিয়েছি বলে যারা প্রচার করছে, তারা আসলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষের একটি বই নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতে চায়। তারা বিজেপি আর সঙ্ঘ পরিবারের নিন্দা না করে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লেখা একটি বই এবং বইয়ের লেখকের নিন্দা যখন করে, আমার সন্দেহ হয় আদৌ তারা আমার বইটি পড়েছে কী না। ধর্মীয় মৌলবাদীর পক্ষে একটি শব্দও কি ওই বইয়ে আছে? নেই। আবারও বলছি, সঙ্ঘ পরিবার যদি আমার বইটি তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে, এটি তাদের অসততা। লজ্জার বা তার লেখকের নয়। তারা নিশ্চয়ই জানে যে লজ্জার বক্তব্য তাদের পক্ষে যায় না। ধর্মের অপর নাম মনুষ্যত্ব হোক, এই কথাটি লজ্জার প্রথম পাতায় লেখা।’
‘আর এসএসের পাঞ্চজন এবং অর্গানাইজারে আপনার উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ অংশ ছাপা হচ্ছে। বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সেই উপন্যাসটিকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল, পরদিনই দেখা গেল, কলকাতার রাস্তায়, ফুটপাতে, পানের দোকানে দোকানে লজ্জা বিক্রি হতে শুরু হল। কেউ কি আপনার উপন্যাস ছাপার অনুমতি নিয়েছে?’
‘অবশ্যই না। কোনও ধর্মীয় রাজনৈতিক দলকে আমি দিই নি লজ্জা ছাপতে, দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কেবল লজ্জা কেন, আমার কোনও বই ছাপার কোনও অধিকার তাদের নেই।’
‘তাহলে আপনি পাঞ্চজন্য আার অর্গানাইজারের বিরুদ্ধে মামলা করছেন না কেন?’
‘মামলা করবে আমার পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশক, যারা লজ্জার সত্ত্ব কিনে নিয়েছেন। তাদেরই দায়িত্ব অন্য ভাষায় অনুবাদ করার আর ছাপার অনুমতি দেওয়া। এতে যদি কোনও রকম সমস্যা হয়, তবে তারা মামলা করবেন। করেছেনও তো এর মধ্যে। যারা অবৈধভাবে লজ্জা ছেপেছিল, তাদের পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।’
‘আমাদের মনে হয় আপনার উপন্যাস এখানকার হিন্দু আর ওখানকার মুসলমানদের অসুবিধেয় ফেলছে।’
‘আপনাদের মনে হওয়ার পেছনে কিছু গণ্ডগোল আছে। আমি এ দেশের এক প্রগতিবাদী শিক্ষিত পরিবারের গল্প বলেছি লজ্জায়। যে পরিবারটি সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার এবং যে পরিবারের একটি নাস্তিক যুক্তিবাদী ছেলে ক্রমে ক্রমে হিন্দু হয়ে ওঠে, সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে, নষ্ট হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র তাকে নষ্ট করে, সরকার নষ্ট করে, দিনে দিনে বেড়ে ওঠা ধর্মীয় মৌলবাদ তাকে নষ্ট করে। সে পরাজিত হয়। এ দেশের অনেক হিন্দুই ধীরে ধীরে মানুষ থেকে হিন্দু হয়ে উঠছে, তারা পরাজিত হচ্ছে রাষ্ট্রধর্মের কাছে, তারা পরাজিত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে, ব্যবসা বাণিজ্যের ধর্মীয় বৈষম্যের কাছে। তারা এ দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। সত্য কথা বলব না কেন? সত্য চিরকালই সম্মানিত হবে। সত্য নিয়ে অঘটন যারা ঘটায়, দোষ তাদের, দোষ সত্যের নয়। যারা সত্যকে দোষ দেয়, তারাই ওই অঘটনঘটানেওয়ালাদের সমর্থন করে। এখানকার হিন্দু অসুবিধেয় পড়বে, এটি একটি বাজে এক্সকিউজ। যারা সুবিধের জন্য মুখ বুজে থাকা মঙ্গল বলে মনে করে, তারা মানুষের শক্তি ও সাহসকে ধ্বংস করে দেয়। তারা ভীতু,ভোগী। তারাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে ক্ষতির কারণ। তারা ভাবে ভুলগুলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে বিপদ হবে। ওখানকার মুসলমানদের অসুবিধের প্রসঙ্গে একই কথা খাটে।’
‘অদূর ভবিষ্যতে আপনার লেখাকে কেন্দ্র করে কোনও অঘটন যদি ঘটে, কী করবেন? লজ্জার দায় মেনে নেবেন?’
‘লজ্জার কারণে অঘটন ঘটবে কেন? অঘটন ঘটবে অঘটন যারা অহরহ ঘটায় তাদের দ্বারা। লজ্জা হচ্ছে একটি মানবিক আবেদন, আর যেন অঘটন না ঘটে। মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ যেন থাকে। ধর্মের অপর নাম যেন মনুষ্যত্ব হয়।’
‘আপনার উপন্যাস একদর্শী। আপনি দাঙ্গা, ধর্ষণ, হত্যা ও উপাসনাগৃহের ভাঙচুরের বিস্তর বিবরণ দিয়েছেন।’
‘হ্যাঁ দিয়েছি। ওগুলো ঘটেছে বলে দিয়েছি। আমি তো কিছু বানিয়ে দিইনি।’
‘দাঙ্গার বিরুদ্ধে সুস্থ মানুষের প্রতিরোধের বয়ান নেই কেন? এটি কি ইচ্ছাকৃত?’
‘একটি পরিবারের স্মৃতি স্বপ্ন আনন্দ বেদনার কথা লজ্জায়। সেই পরিবারের লোকেরা যেভাবে ঘটনাগুলো দেখেছে, সেভাবেই বর্ণনা করেছি। তারা যেটুকু প্রতিরোধ দেখেছে, নিশ্চয়ই সেসব প্রতিরোধের কথা আছে লজ্জায়। মানববন্ধনের কথা আছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিছিল হচ্ছে, সে কথা আছে। মুসলমান ছেলেরা সুরঞ্জনকে নানাভাবে সাহায্য করে এসবও আছে। সুধাময় তাঁর ছেলে সুরঞ্জনকে বলেন, এ দেশের মানুষ কি রাস্তায় নামছে না? প্রতিবাদ করছে না? কাগজে তো বিস্তর লেখা হচ্ছে। এখনও তো অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলছে। এই শক্তিটি কি সব দেশে আছে? প্রতিবাদ করার অধিকার কি সবাই পায়। এখানে তো হচ্ছেই প্রতিবাদ।
আসলে কী জানেন, এ দেশে সাতই ডিসেম্বর থেকে শুরু করে একটানা সাতদিন যে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ঘটে গেছে তার তুলানায় সুস্থ মানুষের প্রতিরোধ খুবই সামান্য। যদি সন্ত্রাস যেটুকু ঘটেছে, ঠিক সেটুকুই যদি প্রতিরোধের বয়ান করতাম, তবে মিথ্যাচার হত। জিজ্ঞেস করেছেন, এটি ইচ্ছ!কৃত কী না। হ্যাঁ ইচ্ছ!কৃত। আমি সত্য বয়ান করতে খুব ইচ্ছ! করি। আমি ভেবে দেখি না, কারা এই সত্য নিজ স্বার্থে ব্যবহার করবে, কারা অনুবাদ করবে, কারাই বা অন্যের ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে কুৎসা রটাবে।’
‘শুনেছি, আমরা খবরও করেছি, আপনি উপন্যাসটিকে আরও বড় করে লিখেছেন। এতে কি ঘটনা ও চরিত্রের রদবদল ঘটেছে? দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নিখুঁত ছবিটি কি আশা করব?’
‘লজ্জাকে খানিকটা বড় করেছি। এতে মূল ঘটনায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু চরিত্র বেড়েছে। চরিত্রগুলোর সংলাপ বেড়েছে। সন্ত্রাসের খবর আরও আছে, আরও কষ্ট, আরও বেদনা আছে। প্রতিবাদও আছে, যেটুকু হয়েছে প্রতিবাদ সেটুকই আছে।’
‘নতুন করে লেখার কারণটি কি?
‘আমি খুব কম সময় নিয়ে লজ্জা লিখেছিলাম। ভেতরের কষ্টগুলো যেন বুক ছিঁড়ে বেরিয়েছিল। পরে, যখন বই হয়ে বেরোবার পর পড়ে দেখলাম, দেখলাম অনেক জায়গায় ভাষার দুর্বলতা রয়ে গেছে। ভাষায় কি আর সব প্রকাশ করা যায়। সব ক্রন্দন? তো, বাক্যগুলো সংশোধন করতে গিয়ে ভাবলাম, আরও কিছু চরিত্র ঢোকালে মন্দ কী!’
‘আপনার উদ্দেশ্য মহৎ আমরা বিশ্বাস করি। আপনার কি কখনও মনে হয় না, তাৎক্ষণিক আবেগ ও তাড়াহুড়োয় আপনি ভুল কৌশলের শিকার হয়েছেন! যেমন অহিন্দু সুরঞ্জন হিন্দু হয়ে উঠল, বাংলাদেশকে গালি দিল,দেশ থেকে পালিয়ে যেতে চাইল, ধর্ষণের মত অপরাধ করে বসল। আপনার লেখায় আগে এমন পরাজয়মনস্কতা দেখিনি। আপনিও কি হার মানছেন?’
‘আমি কৌশলে বিশ্বাসী নই। ডিসেম্বরের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস আমি নিজ চোখে দেখেছি। লজ্জা আমার তাৎক্ষণিক আবেগের ফসল নয়। এটি আমাদের সকলের পরাজয়ের ইতিহাস। এটি আমাদের সবার লজ্জা। সবার গ্লানি। যে কোনও সুস্থ সচেতন মানুষের জন্য এই পরাজয় অত্যন্ত মর্মান্তিক। মানুষ সুরঞ্জন হিন্দু হয়ে উঠছে, মানুষ হায়দার মুসলমান হয়ে উঠছে, দুটোই একই রকম গ্লানিকর। মনুষ্যত্বের চেয়ে ধর্ম যখন প্রধান হয়ে উঠছে, আমি তখনই দায়িত্ব অনুভব করেছি প্রতিবাদের। লজ্জা লেখার অনেক আগে থেকেই আমি প্রতিবাদ করছি এসবের। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লজ্জা হচ্ছে তীব্র প্রতিবাদ। লজ্জায় সুরঞ্জনের বাংলাদেশকে গালি দেওয়া মানে ভাষা আন্দোলন করা, মুক্তিযুদ্ধ করা সাহসী প্রত্যয়ী সেকুলার বাংলাদেশের ধীরে ধীরে ইসলামি হয়ে ওঠা, সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠাকে গালাগাল। রাষ্ট্রের কাঠামো থেকে সত্যিকার গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর বাঙালি জাতীয়তাবাদ ঝরে গেলে সুস্থ সচেতন যে কোনও মানুষ সে কায়সার হোক, সুরঞ্জন হোক বাংলাদেশকে গালি দিতেই পারে। তারা দেশকে ভালবেসেই দেশের সমালোচনা করছে। তারা দেশকে গড়বে, আর দেশ যদি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, তবে গালি দেবে না! আসলে দেশ তো আর আপনাতেই নষ্ট হয় না, কিছু লোক নষ্ট করে দেশকে। কিন্তু সেই কিছু লোক যখন দেশের বেশির ভাগ মানুষকে প্ররোচিত করে নষ্ট করতে, তখন দেশের সৌন্দর্য বলে কিছু আর থাকে না। দেশ আর দেশ থাকে না। সুরঞ্জন তার দেশকে ভালবাসে বলেই কষ্ট পায়, গাল দেয়। এ তার মাতৃভূমি বলেই সে দাবি করে নিরাপত্তা, মান সম্মান। সুরঞ্জনের ব্যর্থতা, পালিয়ে যাওয়া, মুসলমান মেয়ে ধর্ষণ করা, এগুলো কি আমি চাই? চাই না। চাই না বলেই আমি তার অধঃপতনের, তার সর্বনাশের প্রতিবাদ করি। চাই না বলেই আমাকে লজ্জা লিখতে হয়। আমারও তো প্রশ্ন, সুরঞ্জনরা যাচ্ছে কেন? বাংলাদেশকে অনেক হিন্দু ভারতে চলে গিয়ে হিন্দু মৌলবাদী দলে নাম লেখাচ্ছে। কেন? সুরঞ্জনের মত প্রতিভাবান দেশপ্রেমিক ছেলে কেন দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়? ্দেশে থেকে লড়াই করবার মনোবল সুরঞ্জনরা হারাচ্ছে কোথায়? আমার জিজ্ঞাসা তো এটিই। এই প্রশ্নের কোনও উত্তর সরকারের কাছে নেই বলে লজ্জা নিষিদ্ধ করতে হয়। ছাই দিয়ে ঢাকতে হয় আগুন।
আমি পরাজয় মানিনা। মানিনা বলেই আমাকে লজ্জা লিখি। লজ্জা আমার সমাধান নয়। লজ্জা আমার প্রতিবাদ। পরাজয়মনস্ক কখনও ছিলাম না। এখনও নই। বৈষম্য তুলে ধরবার কারণ, এই বৈষম্য আমি মানতে চাই না। মানব না।’
‘সত্যি কি এভাবে হিন্দুরা বাংলাদেশকে গালি পাড়ে? কথায় কথায় অভিশাপ দেয়?’ ‘সুরঞ্জন আর সাধারণ হিন্দুর মত ছিল না। সুরঞ্জনের কোনও ধর্ম বিশ্বাস ছিল না। নাস্তিক ছিল সে। কিন্তু সুরঞ্জনকেই হিন্দু বলে চিহ্নিত করেছে তার আশেপাশের সাম্প্রদায়িক লোকেরা। দেশ নিয়ে সুরঞ্জনের অনেক স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সুরঞ্জনের মন এমনই বিষাক্ত হয়ে ওঠে যে সে দেশকে গাল দেয়। সুরঞ্জন কোনও বৈষম্য মানতে চায় নি বলে গাল দিয়েছে। অনেক হিন্দুই আছে, বৈষম্য দেখেও মুখ বুজে থাকে। মনে মনেও দেশকে গাল দেওয়ার সাহস নেই। হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, গাল দেওয়াকে আমি পছন্দ করি কী না। না অবশ্যই না। কিন্তু সুরঞ্জন দেয় কেন গালি, যে সুরঞ্জন তার দেশকে খুব ভালবাসত! এর পেছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে, কারণগুলো আলোচনা না করে একটি বিভ্রান্ত শোকে দুঃখে ক্ষোভে উন্মাদ হয়ে যাওয়া এক প্রতারিত ছেলে মুখে কি উচ্চারণ করল, সেটি বড় বিষয় হয় কেন!’
‘আমাদের মনে হয় গোটা উপমহাদেশ আজ ভয়ংকর অসুখে আক্রান্ত। বিবেক কোথাও কোথাও স্তব্ধ। বিভ্রান্ত। বিভ্রান্তির হাত থেকে আপনারও কি রেহাই নেই?’
‘লজ্জায় আমার বিবেক সবচেয়ে বেশি শুদ্ধ। পরিষ্ফুট। স্পষ্ট।’
মাত্র সাতদিন আগে সিলেটের সাহাবা সৈনিক পরিষদ একটি ফতোয়া দিয়েছে আমার বিরুদ্ধে। ফতোয়া প্রসঙ্গও তোলেন বাহারউদ্দিন।
‘রুশদি নিজের লেখার পক্ষে দাঁড়ান নি। ক্ষমা চাইলেন। কলমা পড়ে মুসলমান হলেন। আপনার অবস্থা রুশদির চেয়ে করুণ। আপনার পাশে সরকার নেই। বিরোধীরাও নেই। লেখকরাও মুখটি সেলাই করে বসে আছে। আপনি এত একা কেন? একাকীত্ব, ভেতর বাইরের চাপ আপনাকে যদি ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে, কী করবেন?’
‘আমি একা নই। হাজার হাজার পাঠক আছে আমার। আমি যে কথা লিখি, তা সরকারের কাছে যেরকম অগ্রহণযোগ্য, বিরোধীদলের কাছেও সেরকম। দু দলের কেউই ধর্ম বিসর্জন দেবে না। ধর্ম তাদের খুব বড় হাতিয়ার। প্রগতির পক্ষের লেখকরা মুখ সেলাই করে বসে আছেন, এ কথা সত্য নয়। লেখক শিবির, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সিলেটের ফতোয়াবাজ মৌলানাদের তীব্র নিন্দা করেছে। লজ্জা নিষিদ্ধ হওয়ার পর অনেক লেখকই সরকারের সাম্প্রদায়িক আচরণের প্রতিবাদ করেছেন। যারা মুখ খোলে না, তারা কোনও কিছুতেই মুখ খোলে না। কোনও ঝুঁকিই নেয় না। উজানে চলবার মন সবার থাকে না। যেদিকে হাওয়া সেদিকে ছুটবার প্রবণতা বেশির ভাগ মানুষের। ক্ষমা আমি কোনওদিনই চাইব না। রুশদি চেয়েছেন, সে রুশদির নির্বুদ্ধিতা। আমি মরে যাবো, কিন্তু কখনও ক্ষমা চাইব না।’
‘বিপদ এলে দেশ ছেড়ে পালাবেন, অন্য কোনও দেশে আশ্রয় খুঁজবেন?’
‘আমি কি কম বিপদের মধ্যে আছি! যত বিপদই আসুক, আমি কখনও দেশ ছেড়ে পালাবো না। আমার ফাঁসির জন্য মোল্লারা একজোট হচ্ছে। আমি তবু শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার আদর্শে আমি চিরদিনই অটল থাকব।’
‘আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশে লড়াইয়ের শক্ত জমিটি নড়বড়ে হয়ে উঠছে? ঘাতক জামাতের হাতে আপনার কি মনে হয় না তুলে দিলেন নৃশংস একটি অস্ত্র?’
‘শক্ত জমিটি খুব নড়বড়ে হয়ে গেছে — এ কথা আমি মানি না। চারদিকে যখন বিরুদ্ধ পরিবেশ, একটি বিন্দু থেকেও তখন লড়াই হয়। হতে পারে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তা-ই প্রমাণ করে। আমরা যারা মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিবাদ ও মানববাদে বিশ্বাসী, তারা লড়াই করছি। লড়াই আমাদের থামবে না। জামাতে ইসলামির হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছি, এ কথা এখানকার কোনও শত্রুও বলে না। আপনারাই বলছেন। একই রকম লজ্জা সম্পর্কে এখানকার মৌলবাদিরা যা বলছে, ঠিক একই কথা ওখানে আপনারা বলছেন। স্বাধীনতার শত্রু জামাতিদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। লজ্জা তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার অস্ত্র নয়, লজ্জা তাদের মাথা নুইয়ে দেবার অস্ত্র। দেশ জুড়ে জামাতে ইসলামির রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি উঠছে। এই ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে মধ্যপ্রাচ্যের টাকা আর অস্ত্র, তারা নতুন প্রজন্মের হাতেও অস্ত্র আর টাকা দিচ্ছে অঢেল, বিভ্রান্ত করছে আমাদের যুব সমাজকে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় জামাতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন শিবিরের সন্ত্রাস ভয়ংকর হয়ে উঠছে। আমরা বাহান্নর ভাষা আন্দোলন আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ করা জাতি, আমরা কিছুতেই এই মাটিকে অপবিত্র হতে দেব না।’
এ তো গেল। কিন্তু তারপরও পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু বামপন্থী লজ্জা উপন্যাসটির নিন্দা এতটুকু কমাননি। কিন্তু এঁদের মুখই হাঁ হয়ে থাকে, যখন কমিউনিস্টদের গুরু, স্বয়ং নাম্বুদ্রিপাদ লজ্জাকে একটি খুব মূল্যবান বই বলে উল্লেখ করেন। সংখ্যাগুরুর মানুষ হয়ে সংখ্যালঘুর পক্ষে দাঁড়িয়েছি, এই ব্যপারটিকে তিনি অভিনন্দন জানান। এবং নান্দনিক বিচারে যারা বলছিল বইটি নিকৃষ্ট, তাদের গালেও তিনি একটি শক্ত চড় কষিয়ে দেন। (নাম্বুদ্রিপাদ নান্দনিক বিষয় আমার চেয়ে ভাল বোঝেন হয়ত, কিন্তু আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, তাতে আমি স্পষ্ট বুঝি যে বইটি নান্দনিক বিচারে সত্যিই নিকৃষ্ট।)
আনন্দবাজার পত্রিকা এবং আজকাল এদুটো পশ্চিমবঙ্গের বড় পত্রিকা। আজকাল পত্রিকাটি বামঘেঁষা, আনন্দবাজার ঠিক কী ঘেঁষা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না। তবে একটি জিনিস টের পাই, আনন্দবাজারের নাক খানিকটা উঁচু। আজকালের চেয়ে বেশি চলে বলে সম্ভবত। আনন্দবাজার লেখক তৈরি করে না, তৈরি হওয়া লেখকদের ছাপে।
এদিকে বাংলাদেশের মৌলবাদী দল, কেবল মৌলবাদী নয়, আহমদ ছফা এবং ফরহাদ মজহারের যৌগবাদী দলও যাঁরা আনন্দবাজার গোষ্ঠীকে হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠী বলে বিশ্বাস করে, এবং আমি আনন্দ পুরষ্কার পেয়েছি বলে আমাকে হেন কুকথা নেই যে বলেননি, তাঁরা নিশ্চয়ই পড়ার সুযোগ পাননি আনন্দবাজার পত্রিকার ১৫ অক্টোবর তারিখের সম্পাদকীয়। শিরোনাম তসলিমা ও সঙ্ঘ পরিবার। ‘বাবরি মসজিদের পর ভারতীয় জনতা পার্টি এবার আর এক খেলায় মাতিয়াছে। শুধু ভারতীয় জনতা পার্টি নয়, সঙ্ঘ পরিবার এবার বাংলাদেশের প্রতিবাদী লেখক তসলিমা নাসরিনকে লইয়া এক হীন চক্রান্ত শুরু করিয়াছে। তসলিমা নাসরিনের লজ্জা নামক উপন্যাসটি সরকারি হুকুমে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ বই। ভারতীয় জনতা পার্টি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে, লেখকের অনুমোদন না লইয়া এই বইটি হিন্দিতে অনুবাদ করিয়া নিজেদের এক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছে। এই চৌর্যবৃত্তিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ নাই। বরং আগাম জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বইটির ইংরাজি অনুবাদও তাহারা দলীয় পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিবে। শুধু তাহাই নহে, এই দল এবং তাহার অনুগামী বা পুরোগামী হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি নাকি চারটি রাজ্যের আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে তসলিমা নাসরিনের উপন্যাসটিকে কাজে লাগাইতে পারে। গান্ধী যুগের পর ভারতীয় রাজনীতিতে নীতিবোধ আদর্শনিষ্ঠা, সততা বা শুদ্ধাচার অবশ্যই ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। নীতিহীন রাজনীতি কোন পর্যায়ে নামিতে পারে তাহার নতুন প্রমাণ রচনা করিল হিন্দু মৌলবাদীদের এই সব গোষ্ঠী এবং দল। যে সাহসী লেখক মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বেপরোয়া লড়াই চালাইতে গিয়া কার্যত গৃহবন্দী, মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠী যাঁহার প্রাণদণ্ডের দাবিতে সরব, যাঁহার দেশের সরকার এ ব্যপারে নির্বাক দর্শকের ভূমিকায়, তাঁহাকে প্রতিবেশী দেশের হিন্দু মৌলবাদীরা যখন নিজেদের হীন মতলব হাসিল করিবার জন্য কাজে লাগাইতে উদ্যত তখন বুঝিতে হয়, কপটতা এবং মিথ্যাচার ভারতে একটি প্রধান রাজনৈতিক দলকে কীভাবে গ্রাস করিয়াছে। এই উপমহাদেশে এবং দেশের বাহিরে তসলিমা নাসরিনের লক্ষ লক্ষ পাঠক জানেন, তাঁহার দুঃসাহসিকতার লড়াই শুধু নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, মানবতার মহত্তম আদর্শে অনুপ্রাণিত এই লেখক সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা, ধর্মীয় গোড়ামি ও কুসংস্কার এবং হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত মৌলবাদের বিরুদ্ধে এক আপসহীন সংগ্রামী। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর বাংলাদেশে যাহারা ধ্বনি তুলিয়াছিলেন, আযম আডবাণী ভাই ভাই, তসলিমা নাসরিন সেই মুক্তদৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীকামী এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রগতিশীল বাংলাদেশিদেরই একজন। সঙ্ঘ পরিবার কোন নৈতিকতার বলে তাঁহার রচনাকে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করিতে দুঃসাহসী? এই নির্লজ্জ আচরণের তুলনা নাই। অথচ আশ্চর্য ঘটনা এই, তসলিমা নাসরিনের উপন্যাস লইয়া বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবার যখন অভিসন্ধিমূলক যদৃচ্ছ অপকর্মে ব্যস্ত, এ দেশের গণতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি তখন সম্পূর্ণ নীরব। তসলিমা নাসরিনের মাথার দাম ঘোষিত হইবার পর এ দেশের অনেক মহিলা সংগঠন এবং লেখক বুদ্ধিজীবীদের একাংশ তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। কিছু কিছু বিক্ষোভ বিবৃতিও দেখা গিয়াছে। তাহা যথেষ্ট কি না সে প্রশ্ন অবশ্য থাকিয়াই যায়। কিন্তু সঙ্ঘ পরিবার তাঁহার বইটিকে লইয়া যে কদর্য কাণ্ড চালাইতাছে, এ যাবৎ তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। অথচ ভারতীয় জনতা পাটিং এবং সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে নাকি আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দলগুলি খুবই তৎপর! সঙ্ঘ পরিবারের এই কৌশলটি তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গেল, কোনও প্রতিবাদ বা প্রতিকারের কথা কোনও মহল হইতে উচ্চারিত হইল না, ইহা কি বিস্ময়কর নয়? তসলিমা নাসরিন অযোধ্যাকাণ্ডের পর যদি কিছু সত্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও অবশ্যই উঠিতে পারে, সেদিনের বাংলাদেশের ওই পরিস্থিতির জন্য সঙ্ঘ পরিবারের যে স্থূল হাত বাবরি মসজিদ ধ্বংস করিয়াছে তাহাও কি দায়ী নয়? শুধু বাংলাদেশ কেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর এই দেশে যত কিছু কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহার দায়ই বা হিন্দু মৌলবাদীরা অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া? অথচ এই ভণ্ডদের এমনই ঔদ্ধত্য যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের তরফে তসলিমা নাসরিনের সাহসী, মানবিক দলিলটি আজ তাহারা এ দেশের তথাকথিত হিন্দু জাগরণের সপক্ষে ইস্তাহার হিসাবে ব্যবহার করিতে চায়? তসলিমা নাসরিন স্পষ্ট ভাষায় ওই বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শুরু করিয়া শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত জানাইয়া গিয়াছেন, লজ্জার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সব ধর্মের মৌলবাদীদের অধার্মিক এবং অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে। দুঃখের বিষয়, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং বিজ্ঞ কলমধারী এই পরিণতির জন্য দায়ী করিতেছেন লজ্জার লেখক তসলিমা নাসরিনকেই। তাঁহাদের একটি বক্তব্য, তসলিমা নাসরিন কি এ সময়ে এ বই না লিখিলেই ভাল করিতেন না? আমাদের বুদ্ধিজীবীরা আজ কোন পর্যায়ের জীবে পরিণত, এই একটি ধারণা হইতেই তাহার ইঙ্গিত মেলে। বুদ্ধিজীবীদের একাংশের এই পরামর্শ যদি সর্বদেশে সর্বকালে অতি অসাবধানী লেখকরা মানিয়া লইতেন, তবে পৃথিবী হয়ত অনেক যুগান্তকারী রচনা হইতেই বঞ্চিত হইত। তাঁহাদের আর এক বক্তব্য, তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশের প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে তাঁহার গ্রন্থে পরোক্ষে অপমান করিয়াছে। ইহাও অসত্য। সত্য ঘটনা এই, তাঁহাদের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা, সাহসিকতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের একাংশ বাবরি মসজিদের ঘটনার পর অপমানিত, অত্যাচারিত। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের আপৎকালে যে সীমাবদ্ধতা বারবার দেখা যায়, তসলিমা নাসরিনের রচনা সে দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বস্তুত, তাঁহার বিরুদ্ধে বি জে পির পৃষ্ঠপোষণার অভিযোগ না আনিয়া আমাদের অতিবুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবীদের বোধহয় উচিত ছিল সন্ধানী আলোটি একবার নিজেদের দিকে ঘোরানো। তসলিমা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি উদঘাটন করিয়াছেন। আমরা কি এ দেশে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিতাম না? দাঙ্গার সময় এ দেশের সংখ্যালঘুদের মানসিক অনুভূতি কী, সে কথা আমরা কয়জন বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে আমরা মিছিল করি, বিবৃতি দিই, পোস্টার ছাপাই, ইস্তাহার বিলি করি – সবই ঠিক। প্রগতিশীল সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মানুষের সংখ্যা অগণ্য, ইহাও ঠিক। তাহা সত্ত্বেও বামপন্থী রাজত্বের মধ্যেও সেদিন কি এই রাজ্যেই বেশ কিছু মানুষ দাঙ্গায় প্রাণ হারান নাই? এই প্রশ্ন তুলিলে যদি আমাদের দেশের প্রগতিশীল শক্তি এবং বুদ্ধিজীবী মহলের অবমাননা না হয়, তবে তসলিমা নাসরিনের বেলাতেই বা তাহা অপরাধ হইবে কেন? তসলিমা নাসরিন অতএব আমাদের লজ্জা নয়, আমাদের প্রকৃত লজ্জা বুদ্ধি এবং কপট যুক্তির ছলে ভাবের ঘরে এই চুরি।’
২১. মানবরূপী শয়তান
নির্বাচিত কলাম বেরিয়েছে একানব্বই সালে ফেব্রুয়ারিতে। আটানব্বই আর নব্বই সালে লেখা কলামগুলো নিয়ে। কলামগুলো নির্বাচিত না বলে প্রাপ্ত বলা যায়। খোকা যে কটি কলাম সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, সেগুলোই বইয়ে দিয়েছেন। অনেক লেখাই হারিয়ে গিয়েছে। আমি লেখাগুলো জমিয়েও রাখিনি, কারণ বই হয়ে কখনও বেরোবে এই স্বপ্নও তো কোনওদিন দেখিনি। বইটি বেরোবার পর যারা বইএর লেখার সঙ্গে এক মত হতে পারেননি, তাঁরা পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি করেছেন। কেউ কেউ আবার অতি উৎসাহে গোটা বই লিখে ফেলেছেন। বইগুলোর কিছু কিছু হাতে আসে, কিছু আসে না। তিরানব্বইএর ফেব্রুয়ারিতে জ্ঞানকোষের প্রকাশক উচিত জবাব নামে একটি বই আমাকে দিলেন। লেখকের নাম মোঃ মোকাদ্দেস হোসাইন। নির্বাচিত কলাম পুরোটাই ছেপে, আমার প্রতিটি রচনার নিচে তাঁর নিজের মন্তব্য সেঁটে মোকাদ্দেস হোসেন বই বের করেছেন। নির্বাচিত কলাম তো বিক্রি হচ্ছেই, উচিত জবাবও নাকি কম নয়। নির্বাচিত কলামের চেয়ে উচিত জবাব দশ টাকা কম, বিক্রি না হবার কোনও কারণ নেই, পাঠক কম দামে আমার লেখাগুলো পাচ্ছে, বাড়তি একটি জিনিসও পাচ্ছে, সে মন্তব্য। এ বই যে কিনবে, তার আর নির্বাচিত কলাম কেনার দরকার নেই, কারণ এই বইএর ভেতরেই আমার পুরো বইটিই আছে, প্রকাশক বললেন। প্রকাশক ব্যবসার কথা ভাবলেন। আমি ব্যবসার কথা নয়, ভাবলাম মোকাদ্দেস হোসাইনের অসততার কথা। গ্রন্থসত্ত্র আইন বলে কোনও আইন এ দেশে আছে কি না সে ব্যাপারে আমার জানতে আগ্রহ হয়। নাহিদের কাছে জানতে চাই ও জানে কি না এ বিষয়ে। মেয়েটি আইন নিয়ে লেখাপড়া করেছে, আমার বাড়িতে প্রায়ই আসে। এমনি আসে। আমার লেখা ভাল লাগে বলে আসে। ওই নাহিদই একদিন অতি উৎসাহে বলল মামলা করার কথা। মামলা সম্পর্কে আমার চেয়ে কম জানোয়া আর কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। ব্যপারটিতে জড়াতে আমি গড়িমসি করি, কিন্তু নাহিদ বলে যে আমার কোনও সাতে পাঁচে না থাকলেও চলবে, সে নিজে রাবেয়া ভূঁইয়াকে দিয়ে মামলা করাবে। কিন্তু! কিন্তু কি! শুনেছি মামলায় নাকি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা যায়! নাহিদ রাবেয়া ভূঁইয়ার সঙ্গে দেখা করে এসে আমাকে জানিয়ে দিল, ব্যারিস্টার কোনও টাকা নেবেনই না। রাবেয়া ভূঁইয়াকে লোকে চেনে। তিনি একসময় আইন মন্ত্রী ছিলেন। এমন নামী ব্যারিস্টার গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন ভাঙার অপরাধে উচিত জবাবের প্রকাশকের বিরুদ্ধে লড়বেন, টাকা পয়সা ছাড়া লড়বেন, আর আমার মোটে কিμছু করতে হবে না, হোক না! রাজি হই। রাজি হওয়ার পর পরই অবশ্য নাহিদের অনুরোধ একটু একটু করে তীব্র হতে থাকে, একদিন দেখা অন্তত করুন, এ কাজে ও কাজে কেরানিকে টাকা পয়সা দিতে হবে, দিন। আমাকে নিয়ে রাবেয়া ভূঁইয়ার সঙ্গে একদিন দেখা করিয়েও আনল। গ্রন্থস্বত্ত্ব আইনের কথা তখন তাঁর মুখেই শুনি যে বই এর স্বত্ত্ব নিয়ে এ দেশে এ অবদি কেউ মামলা করেনি। হয়ত ইট কাঠ আম কাঁঠাল এমনকি আমস্বত্ত্বেরও স্বত্ত্ব থাকে, কিন্তু গ্রন্থের থাকে না। আইনত, বইএর প্রথম পৃষ্ঠায় যার নামই থাক গ্রন্থসত্ত্বাধিকারী হিসেবে, রচয়িতার রয়্যালটি সেই সত্ত্বাধিকারির হাতে কেউ পৌঁছোবে না যতক্ষণ না সত্ত্ব্বাধিকার নিবন্ধিভূক্তি হচ্ছে। রাবেয়া ভূঁইয়া আমাকে পাঠালেন শেরে বাংলা নগরের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সত্ত্বাধিকার আপিসে স্বত্ত্বাধিকার নিবন্ধিকরণের জন্য। মার্চের ষোল তারিখে আবেদন করলাম, নথিভুক্ত হয়ে বেরোল মে মাসের পনেরো তারিখে। রাবেয়া ভূঁইয়া এরপর মামলার আরজি লিখে নিজেই পুরোনো ঢাকার দায়রা জজ আদালতে যাতায়ত শুরু করলেন। আরজির বিষয়, নকল বইটির প্রকাশনা, পরিবেশনা, মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হোক। যুক্তির কথা, কারণ ওই লোককে আমি অনুমতি দিই নি নির্বাচিত কলামের অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত নতুন করে তাঁর বইয়ে ছাপতে। লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাও দাও, সমালোচনা করতে চাইলে থান ইটের আকারে পুরো সমালোচনার বই বের করা যায়, আহমদ ছফা এবং অন্যরা যেমন করেছেন। সমালোচনার নামে যে গালাগাল করা হয়েছে আমাকে, সেটি আমাকে আহত করেনি, অহরহই এমন গালাগাল ইনকিলাব জাতীয় পত্রিকার পাতা জুড়ে প্রকাশ হয়, এ নতুন কিছু নয়। আর গাল কারা দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে সে ব্যাপারে আমার ধারণা আছে বলেই আমার গায়ে পায়ে কোথাও কোনও দাগ পড়ে না, মনে তো নয়ই। কিন্তু আমার বইটি চুরি করবে কেন! মামলা নিয়ে নাহিদের উত্তেজনা এমনই লাগামছাড়া হয়ে ওঠে যে মামলার শুনানির দিন একবার আমাকে তার জোর জবরদস্তিতে যেতেই হল আদালতে। আদালত জুড়ে মহাদাপটে বিচরণ করছেন অসংখ্য টুপি দাড়িঅলা লোক। মোকাদ্দেস হোসাইন তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে আদালতে উপস্থিত। বিবাদির পক্ষে ব্যারিস্টার কোরবান আলী লড়ছেন। ব্যারিস্টার কোরবান আলী তাঁর জীবনটি ইতিমধ্যে কোরবান করে দিতে চাইছেন আমার বিরুদ্ধে লড়ে। পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে বক্তব্য বিবৃতি যখনই বেরোয়, ব্যারিস্টার কোরবান আলীর নামটি জ্বলজ্বল করে। যোগ্য ব্যারিস্টার বটে উচিত জবাবের জন্য। আমাকে উচিত শাস্তি না দিয়ে তিনি ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত যা হল তা দুঃখজনক। মামলা আমার পক্ষে যায়নি। আমার আরজিই বাতিল বলে ঘোষণা করা হল। এরপর মোকাদ্দেস হোসাইন কেবল উচিত জবাব বইটি বাজারে পূনর্মুদ্রণ করে ক্ষান্ত হননি, দুপক্ষের আরজি আর আরজির জবাব ছেপে লিফলেটও বিলি করতে লাগলেন। একটি লিফলেটে লেখা, ‘ প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা! মানবরূপী শয়তান হতে সাবধান!! উচিৎ জবাবের লেখক মুহম্মদ মোকাদ্দেস হোসাইন কী এমন জবাব দিলেন যে বিজাতীয় বিধর্মীদের কর্তৃক আনন্দ পুরষ্কৃত চরম ইসলাম ও পরম পুরুষবিদ্বেষী তসলিমা নাসরিনের সোঁচালো কলম এমনই ভোঁতা হয়ে গেছে যে তিনি লেখার জবাব লেখনীর মাধ্যমে না দিতে পেরে শেষে বাধ্য হয়েছেন উচিৎ জবাবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার আশ্রয় নিতে। উচিৎ জবাব এখন ফটোকম্পোজের চেয়েও নিখুঁত ঝকঝকে ও তকতকে টাইপে পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও আরো অকাট্য যুক্তি নির্ভর জবাবে প্রকাশিত হয়েছে — যাতে পাবেন নির্বাচিত কলাম নামের বিতর্কিত বইটির প্রতিটি কলামের নিচে তার দাঁত ভাঙা উচিৎ জবাব..!!’ আমার আরজির জবাবে বিবাদিগণেরও পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার কোরবান আলী বলেছেন, ‘বিবাদিগণ বাদিনীর অশ্লীল, অশ্রাব্য, অসামাজিক, নোংরা, ধর্ম-বিরুদ্ধ, দেশদ্রোহী ও কুরুচিপূর্ণ যৌন আবেদনে ঠাসা ভরপুর এহেন জঘন্য পুস্তক নকল করার হীন উদ্দেশ্যে কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই, বরং এ জাতীয় ধৃষ্টতাপূর্ণ লেখার তীব্র সমালোচনা করিয়া চিরাচরিত রীতিতে জবাব দিয়াছেন। বাদিনী কপিরাইট অফিসকে ভুল বুঝাইয়া এই কুরুচিপূর্ণ পুস্তক এর কপিরাইট নিবন্ধন করিয়াছেন। এই ধরনের পুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণ বাংলাদেশ দন্ডবিধির ২৯২ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্যে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টির লক্ষ্যে সভ্য সমাজকে বাদিনী অসভ্যতার দিকে নিয়া যাইতেছে। বিবাদির পরিচয়, ১ নং বিবাদি একজন প্রথিতযশা লেখক ও প্রকাশক, তিনি ছাত্র জীবনে একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি জীবনের শুরুতেই মেধাবী ছাত্র হিসাবে বরাবরই সরকারি বৃত্তি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ৫ টি লেটার সহ স্টারমার্ক ও স্কলারশিপ পাইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি দেশের খ্যাতনামা বিদ্যাপীঠ ঢাকা কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আই.এস.সি পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পাশাপাশি লেখালেখি ও প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে জড়াইয়া পড়েন। ১৯৮৭ ইং সন থেকেই বই লেখায় তিনি মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর নীহারিকা মাধ্যমিক ভূগোল গাইড, নীহারিকা মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান গাইড ১ম পত্র ও ২য় পত্র ইত্যাদি পুস্তক সমূহের তিনি সফলকাম রচয়িতা ও প্রকাশক। তাহার প্রকাশিত ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের গাইড বই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদল লাভ করিয়াছে। তিনি জাতি গঠনে গঠনমূলক ও সৃজনশীল লেখার দ্বারা কিশোর ও তরুণদের দিক নির্দেশনা দিয়া জাতির খেদমতে ব্যাপৃত আছেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ সৃজনশীল লেখক পরিষদের সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাংলাদেশের সৃজনশীল লেখক লেখিকাদের কল্যাণে নিয়োজিত আছেন।’
বাকি বিবাদিগণও বেশ সম্মানীয় বটে। তাঁদের বক্তব্য, ‘বাদিনী বিভিন্ন কলামে ইসলাম ধর্মকে কটাক্ষ করিয়া কথা বলিতে দ্বিধা করেননি, এমনকি পবিত্র কোরান শরিফ ও হাদীস শরিফের বিকৃত ব্যাখ্যা পর্যন্ত করিয়াছেন। পবিত্র কোরান শরিফকে কটাক্ষ করিয়া ইহাকে স্বামীদলভুক্ত পুরুষ রচিত বলিয়াছেন, ইহার পাঠক ও অনুসারীকে তিনি বর্বর ও মূর্খ বলিয়া গালি দিয়াছেন। বাদিনীর হঠাকারিতার মাত্রা এতই ভয়ানক যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সম্প্রতি বাধ্য হইয়াছেন তাহার লজ্জা নামক বইটি বাজেয়াপ্ত করিতে। পাশাপাশি সমাজ সচেতন বিভিন্ন মহলের জনগণের নিকট হইতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দাবী উঠিয়াছে বাদিনীর নির্বাচিত কলাম ও শোধ গ্রন্থ দুইখানি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য। সাম্প্রতিক সিলেট শহরে তথা দেশের সকল সচেতন জনগণের পক্ষ থেকে সাত দিনের মধ্যে তাকে বন্দী করার ও তার সমস্ত কর্ম বাজেয়াপ্ত করার জন্য জোর দাবী উঠেছে। অন্যথায় সিলেট শহর সহ দেশের বিভিন্ন শহরে এর প্রতিবাদে হরতালের ডাক পড়িয়াছে। বাদিনী তাহার বিভিন্ন কলামে নারী স্বাধীনতার নামে পুরুষের বিরুদ্ধে অযথা কটুক্তি ও লাগামহীন অশ্রাব্য ভাষা ব্যাবহার করিয়া শ্রেণী বিদ্বেষ সৃষ্টি করার যথেষ্ট প্রয়াস চালাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, নারীদেরকে কোন অংশেই বা কোন কলামেই সম্মান না দেখাইয়া তাহাদেরকে কলুষিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। বাদিনী তাহার লেখায় মুসলিম পরিবার, সমাজ ও ব্যক্তিবর্গকে অসম্মান করিবার এক জঘন্য ও হীন চেষ্টা চালাইয়াছেন। বাদিনী তাহার লেখায় দেশিয় প্রচলিত স্বাভাবিক নিয়ম নীতি ভঙ্গ করিয়া শালীনতা, ভদ্রতা লংঘন করিয়া কুরুচিপূর্ণ ও নগ্ন যৌন বিষয়ে আলোচনা করিয়া পাঠক সমাজকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন। নির্বাচিত কলামের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিনের সমাদৃত মুসলিম সমাজ ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়াছেন বটে এবং যে কোন দিক নির্দেশনা না দিয়া কল্পিত নারী ঘটিত এক উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনায় ভরপুর অসভ্য সমাজ রূপায়নের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস চালাইয়াছেন। পুরুষের ধর্মীয় বিধান মোতাবেক একাধিক স্ত্রী অনুমতির প্রতি বাদিনী জঘন্যভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামীর উপস্থিতিও সমাজ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে থাকার দাবী করিয়াছেন। যাহা ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে স্ত্রীর জন্য জেনা এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষের পিতৃ পরিচয় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে তদোপরি সুন্দর মানব জীবন ও স্মরাণাতীতকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত মানব সভ্যতা ধুলায় মিশিয়া যাইবে। যে ষড়যন্ত্রের হোতা বাদিনী নিজে। বাদিনী তাহার উক্ত গ্রন্থে জরায়ুর স্বাধীনতার উপরও জোরালো বক্তব্য রাখিয়াছেন। জরায়ু নেহায়েতই নারীদের শরীরে একটি বিশেষ অংশ যার মাধ্যমে মানব জনম ও মানব সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়া আছে। উক্ত তথাকথিত স্বাধীনতার সাথে বাদিনী আল্লাহর স্বাভাবিক সৃষ্টির প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। যার মাধ্যমে বাদিনীর ধর্মচ্যূতি ঘটিয়াছে বিধায় কোরানের আলোকে মুরতাদ হিসাবে অভিশপ্ত সালমান রুশদির ন্যায় মৃত্যুদন্ডের শাস্তি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।’
উচিত জবাবের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। উচিত জবাব বহাল তবিয়তে বিরাজ করে বাজারে। আদালতের মুরব্বীগণ আমার পক্ষে রায় দিয়ে উচিত জবাবকে একটি উচিত জবাব দেবার পক্ষে নন। আমি মানবরূপী শয়তান, তাঁরা আল্লাহর বান্দা, সৃষ্টির সেরা জীব। আমি কেন পেরে উঠব আল্লাহর দয়া যাদের ওপর, তাদের ব্যবসা নষ্ট করতে! আমার ওপর তো আল্লাহ তায়ালার করুণা বর্ষিত হয়নি।
উচিত জবাব হামেশাই দেওয়া হচ্ছে আমাকে। উচিত অনুচিত নিয়ে দুঃখ করে সময় নষ্ট করতে আমার আর ইচ্ছে হয় না। আমার সময়গুলো অন্যভাবে ব্যয় হতে থাকে। কারও জন্য কিছু করে। যা করতে চাই, যেমন করে করতে চাই তা করতে পারি না বলে লিখতে হয়। আমাকে আমূল তোলপাড় করা ভাবনা গুলোর কতটুকুই আর প্রকাশ করতে পারি লিখে! ভাবনা হবে না কেন, প্রতিনিয়তই মেয়েরা লাঞ্ছিতা হচ্ছে, ধর্ষিতা হচ্ছে, খুন হচ্ছে। দেশের ঘটতে থাকা ঘটনাগুলো যেগুলো আমাকে নাড়ায়, কাঁদায়, ভাবায়, ক্ষুব্ধ করে, ব্যথিত করে সেসব নিয়ে লিখি। কোনও গভীর তত্ত্ব কথা নয়। তথ্যবহুলও কোনও প্রবন্ধ নয়। লেখাগুলো একধরনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। গবেষণা করে কিছু বার করা নয়। দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়, পরদিন সে পত্রিকার পাতা বাদামের ঠোঙা হয়ে যায়। সাপ্তাহিকী গুলোয় ছাপা হয়, সপ্তাহ গেলে সেসব কাগজ চলে যায় ময়লা ফেলার বাক্সে। পচা পুরোনো জিনিসের সঙ্গে মিশে যায়। আমার প্রতিদিনকার কলামের টুকরো টুকরো কিছু বাক্য.. .
‘শাহিদা নামের এক ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করে ফেলল লিয়াকত ম্যাজিস্ট্রেট কারণ শাহিদা লিয়াকতের বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। লিয়াকতের সঙ্গে হয়ত শাহিদার বন্ধুত্ব ছিল, এই সম্পর্কের ছুতোয় লিয়াকত জোর খাটিয়েছে। লিয়াকত ভেবেই নিয়েছে সে পুরুষ, সে যা বলবে শাহিদাকে তা-ই শুনতে হবে। শাহিদা শোনেনি সম্ভবত শোনেনি এই জন্য যে সে একজন শিক্ষিত স্বনির্ভর মেয়ে, তার নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের দাম সে দিতে চায়। কিন্তু তা মানবে কেন লিয়াকত, সে পুরুষ, সে তার গায়ের জোর তার ছুরির জোর তার পুরুষঅঙ্গের জোর না খাটালে সে আর পুরুষ কেন! পুরুষ এমনই জন্তু বিশেষ যে দাঁত নখ চোখের হিংস্রতা দিয়ে সে তার পুরুষত্ব জাহির করতে চায়। মনুষ্যত্ব, আমি সবসময়ই দেখেছি পুরুষের মধ্যে খুব কম। মনুষ্যত্বের সঙ্গে পুরুষত্বের বোধহয় চিরকালীন এক বিরোধ আছেই। লিয়াকত যদি বিয়ে করত শাহিদাকে, এরকম আঘাতে আঘাতে শাহিদাকে তিল তিল করে মরতে হত, কেউ দেখতে পেত না তার ভেতরের ক্ষরণ, লোকে ভাবত — কী চমৎকার জুটি! লোকে এখনও চোখে কালি পড়া নিরন্তর মার খাওয়া স্ত্রীদের নির্দ্বিধায় সুখী বলে বিবেচনা করে। লিয়াকত পুরুষের মত পুরুষ। সে পুরুষের যোগ্য কাজই করেছে। নারীকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে।
প্রেম প্রেমই। এর আগে পরে পরকিয়া বা আপনকিয়া শব্দ ব্যবহার করলে প্রেমের মহিমাই নষ্ট হয়। ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদা পরকিয়া প্রেম করত এবং সন্তানটি তার স্বামীর ঔরসজাত নয়, এ নিয়ে পত্রিকাগুলো এখন মুখর। প্রেম সে করতেই পারে, স্বামীর যদি স্পার্মলেস সিমেন থাকে অথবা সে উত্থানরহিত হয়, স্ত্রী তার প্রেমিকের সন্তান গর্ভে নিতেই পারে, মানুষ তার মনে এবং শরীরে কাকে বহন করবে বা না করবে সে একান্তই তার ব্যপার। শাহিদার প্রেম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা মানে তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ শুধু নয়, পদক্ষেপ করাও। অবশ্য জীবিত মেয়েদেরই যেখানে স্বাধীনতা নেই, সেখানে মৃত মেয়ের আবার স্বাধীনতা কি!
বাসাবোয় নিলুফার নামের এক মেয়েকে খুন করেছে তার স্বামী। সেই স্বামী এখন বহাল তবিয়তে আছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে কে আটকায়! তার আছে পয়সার জোর, সবচেয়ে বেশি আছে সরকারের জোর। সরকারের জোর যার আছে, সে যত বড় চোর ডাকাত বদমাশ খুনী হোক পার পেয়ে যায়। সরকার তার পেয়ারা বান্দাদের জন্য বড় শক্ত করে একটি সাঁকো বানিয়েছেন। আল্লাহতায়ালার পুলসেরাতের চেয়ে সরকারের সাঁকো বেশি মজবুত।
মহিলা পরিষদের সদস্যরা উন্মাদ হয়ে গিয়েছে খুকুর ফাঁসি দেবার জন্য। মুনির তার স্ত্রীকে খুন করেছে। মুনিরের ফাঁসি হবে। কিন্তু মহিলা পরিষদের দাবি, খুকুকেও ফাঁসি দিতে হবে। কেন, খুকুকে কেন ফাঁসি দিতে হবে! কারণ খুকু নাকি চরিত্রহীনা ছিল। নিজে বিবাহিতা হয়েও খুকু মুনিরের সঙ্গে প্রেম করেছে, এই তার দোষ। মহিলা পরিষদএর মিছিল যখন আদালত প্রাঙ্গনে গিয়ে খুকুর ফাঁসির জন্য গলা ফাটাচ্ছে, আমি লজ্জায় মুখ ঢেকেছি। খুকুর কেন শাস্তি হবে, খুকুর অন্যায়টি কি? খুকু তো এই খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল না! অক্ষম অথর্ব স্বামী নিয়ে জীবন কাটাতো খুকু, স্বামী দ্বারা লাঞ্ছিত, প্রেমিক দ্বারা প্রতারিত এই অসহায় মেয়েটিকে সারাদেশের মানুষ গাল দিল, জেলে ভরল, খুকু নামটিকে একটি নষ্ট মেয়ের নাম হিসেবে চিহ্নিত করল। খুকুর সঙ্গে মুনিরের ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, থাকতেই পারে। এটি খুকুর দোষ নয়। ভালবাসা কি দোষের জিনিস!
পটুয়াখালির এক লঞ্চযাত্রীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। কোনও ডাকাত নয়, লঞ্চের মস্তান ছেলেরা নয়, মদ্যপ বদমাশরা নয়, ধর্ষণ করেছে ওই লঞ্চে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য যে আনসারদের রাখা হয়েছিল, তারা। তারা পাঁচজন। কুড়ি বছর বয়সী মোসাম্মত বেগমকে জোর করে তাদের কেবিনে নিয়ে ধর্ষণ করে। লঞ্চ ভর্তি লোক, কিন্তু আনসারগুলো এই কাজটি করতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। সেবকদের পুরুষাঙ্গ লঞ্চের ভিড়ের মধ্যে একটি যাত্রীর জন্য উত্থিত হয়েছে। উত্থিত হওয়ায় আমি কোনও আপত্তি করছি না। তারা সেবক হলেও পুরুষ তো, উত্থিত হবেই। মেয়েটি যদি তাদের উত্থানে সাড়া দিত, যদি এমন হত যে পাঁচজনের সঙ্গে সঙ্গমে মোসাম্মত বেগমের আপত্তি নেই তবে এ নিয়ে সারাদেশে কারওরই আপত্তি করবার প্রশ্ন ওঠে না। যে কারও অধিকার আছে যে কোনও সম্পর্কের গভীরে যাওয়া, অবশ্য পরস্পরের যদি সম্মতি থাকে। কিন্তু জোর করে কোনও সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে না। হওয়া উচিত নয় যদি এই সমাজকে সভ্য বলা হয়। সভ্য বলেই তো দাবি করছে সবাই, তবে জোর করে সম্পর্ক সম্ভব হয় কী করে? কী করে একজন যাত্রীকে ধর্ষণের জন্য সেদিন রাষ্ট্র কতৃক নিয়োজিত কিছু আনসার, যে আনসার শব্দের অর্থ য়েচ্ছ!সেবক, উদ্যত হয়? কী করে যাত্রীদের সেবকরাই যাত্রীদের নিরাপত্তার সবচেয়ে অন্তরায় হয়? আনসারদের অপরাধের কোনও শাস্তি হয়নি। আমার ভাবতে অবাক লাগে দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী, ভেবে আশ্চর্য হই এই দেশের বিরোধীদলের নেত্রী একজন নারী। তাঁরা কি এইসব ঘরে বাইরের ধর্ষণের কোনও সংবাদ পান না? নাকি পেলেও তাঁদের অন্তরে কোনও জ্বালা ধরে না, তাঁদের কাছে ধর্ষণ অত্যন্ত উপাদেয় জিনিস বলে মনে হয়, ধর্ষণের জন্য তেমন রুষ্ট হওয়ার তাঁরা দেখেন না কিছু! দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী হওয়ার পরও দেশে অবাধে চলছে বধুহত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড ছোঁড়া, যৌতুকের অত্যাচার, বাল্যবিবাহ। এখনও নারীর বিরুদ্ধে নানা জাতের আইন খড়গ উঁচিয়ে আছে। নারী হয়ে নারীর বেদনা বুঝবার ক্ষমতা যার বা যাদের নেই তাঁরা মানুষের আর কী সেবা করতে পারেন! তাঁরা যদি অত্যাচারিতের পক্ষেই না দাঁড়াতে পারেন, তবে তাঁরা কার পক্ষ নেবার জন্য মহান সেবকের দায়িত্ব নিয়েছেন? ধনীর, অত্যাচারীর, সুবিধাভোগীর, পাপীর? পাঁচ সেবকের ধর্ষণ এমন কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এমন ধর্ষণ হচ্ছেই গ্রামে গঞ্জে শহরে ফুটপাতে লঞ্চে ট্রেনে নৌকোয় জাহাজে। এসবের জন্য শাস্তি হবে না কারওর। এই দেশে ধর্ষণ কোনও শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। মহান সেবকের বন্ধুরা নারীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেবে, সেই ফতোয়া মহাসমারোহে পালন করা হবে। যে দেশে নারীর পক্ষে লেখার অপরাধে পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়, সেই দেশে ফতোয়ার রাজনীতিই বিরাজ করবে, এ আর আশ্চর্য কী! কিছুই অবাক করে না আমাদের। কিছুই আর হতবাক করে না আমাদের। খবরের কাগজে আমরা এইসব চমকপ্রদ সংবাদ দেখি পড়ি ভুলে যাই। কিছুই আমাদের আর কাতর করে না। আমাদের পিঠে কোনও চেতনার চাবুক পড়ে না। কারণ আমরা জেনেই গিয়েছি জনগণের সেবকেরা যখন ধর্ষকের ভূমিকায় নামে, মানুষের সাধ্য থাকে না তাদের শাস্তি দেবার। এদেশে সেবক পাল্টায়, সেবকের চরিত্র পাল্টায় না। সে নারী হোক কী পুরুষ হোক।
কলকাতার ফুলবাগানে ঘুমন্ত এক ফুটপাতবাসিনীকে জোর করে পুলিশ ভ্যানে তুলে থানার ব্যারাকে নিয়ে পুলিশ কনস্টেবল নীলকমল সনাতন আর ভোলানাথ ধর্ষণ করেছিল। নীলকমলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। কিন্তু এ দেশে কোনও ধর্ষকের এরকম শাস্তি কল্পনা করা যায় না। পটুয়াখালির লঞ্চের যে মেয়েটিকে ধর্ষণ করেছিল আনসাররা, বলা হচ্ছে সে নাকি পতিতা ছিল। যেন পতিতা ছিল বলে আনসাররা তাকে ধর্ষণ করবার দাবি রাখে। পতিতা ছিল বলে আনসারদের সাতখুন মাপ। এখানে ফুটপাতবাসি হলে এরকমই অবস্থা হত, বলা হত ফুটপাতে পড়ে থাকা মেয়েকে ধর্ষণ করা এমন কোনও অন্যায় নয়। ধর্ষণ ঘটলে এখনও এদেশে ধর্ষিতাকেই দোষী ভাবা হয়। বলা হয় মেয়েটি প্রভোক করেছিল ধর্ষণ করতে, তার মিটিমিটি চোখের চাওয়া, অকারণ হাসি, উগ্র পোশাক সবই ধর্ষণের অনুকূলে ছিল। এসব যুক্তিকে সমাজে বেশ কদর করা হয়। একজন মেয়ে, তার যদি ইচ্ছে করে সে হাসবে, যেমন ইচ্ছে চলবে, যেমন খুশি তার পোশাক পরবে — এ কারণে তাকে ধর্ষিতা হতে হবে কেন?
আমি যৌন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আর সব স্বাধীনতার মত মানুষের এই স্বাধীনতাও প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের শরীরে জোর জবরদস্তি চলবে কেন? সে ভিখিরি হোক কি পতিতা হোক কি স্ত্রী হোক — সে যদি অনুমতি না দেয় কারও কি অধিকার আছে তাকে স্পর্শ করবার? আমার বিচারে নেই। রাষ্ট্রের বিচারে বরাবরই ধর্ষকরা পার পেয়ে যায়। এতে রাষ্ট্রই নারীর নাগরিক অধিকারে থুতু ছিটোয়। এরপরও এ দেশের নারীরা যদি মুখ ফুটে ধর্ষণের বিচার যাবজ্জীবন করবার জন্য আন্দোলন না করে, আমি তবে সেই নির্বোধ নারীদের বলতে বাধ্য হব, তারা বোধহয় মনে মনে ধর্ষিতা হতেই চায়।
যায় যায় দিন পত্রিকায় আমার নিয়মিত কলামটির নাম আমার মেয়েবেলা। ওতে একবার লিখেছিলাম .. বাসে উঠলেও একটি একলা মেয়ে দেখলে কনডাকটর কোনও মেয়েকে পাশে বসায়, মেয়ে না পাওয়া গেলে বুড়ো পুরুষের পাশে, বড় জোর বাচ্চা কোনও ছেলের পাশে। কনডাকটর নিজে পুরুষ, সেও জানে পুরুষের স্বভাব। তাই সে অথর্ব বা অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পাশে মেয়েদের বসিয়ে স্বস্তি পায়। পুরোনো লেখা নতুন করে স্মরণ করবার কারণ হচ্ছে একটি চিঠি। চিঠি তো দিনে কয়েক শ আসে। সব চিঠি পড়বার সময়ও হয় না। হঠাৎ হঠাৎ কিছু চিঠি চমকে দেয়, কিছু চিঠি ভাবায়, কিছু আবার কাঁদায়ও। মৌ নামের এক মেয়ে কুমিল্লা থেকে আমাকে লিখেছে.. ‘আপনার চলতি সংখ্যার কলামের এক কোণে লেখা ছিল বুড়োরা অথর্ব। এতে আমারও কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমার অবুঝ বেলার ছোট্ট একটা ঘটনা আপনাকে জানাতে ইচ্ছে করছে। প্রতিকারের আশায় নয় — শুধু বলবার জন্য মানুষের কেউ না কেউ তো থাকতেই হয়। আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। বুড়ো মতন এক লোক এলেন আমাদের মফস্বলে, শেক্সপিয়রের গল্প থেকে নৃত্যনাট্য করে ডোনেশন তুলতে। আমি ওতে একটা গানে অংশ নিয়েছিলাম। একদিন রিহার্সেলের পর রাতে জীপে করে সবাইকে পৌঁছে দিতে গিয়ে সবচেয়ে শেষে পৌঁছোলেন আমাকে — সর্বকণিষ্ঠ বলে এবং সেই সুযোগে উনি আঙুল দিয়ে আমার যৌনাঙ্গে চাপ দিতে লাগলেন। আরও বেশি কিছু হবার আশঙ্কায় সে রাতে শুধু মুহূর্ত গুনেছি কখন বাসার গেটটা চোখে পড়বে। পরের দিন বাসায় চলে এলেন ভাল করে গান শেখাতে। আমার মা ডিসটার্ব হবে ভেবে সে ঘরে আর এলেন না। উনি কিছুক্ষণ পর আমাকে বললেন, দাদু তোমার কাছে একটা ছোট্ট জিনিস চাইব, আমাকে ফিরিয়ে দিও না। এবং তারও অনেক পরে আতঙ্কিত আমার পা ফাঁক করে যৌনাঙ্গে একটা চুমু দিলেন। তারপর অনেকগুলো দিন আমার শুধু পানিতে ডুবিয়ে রাখতে ইচ্ছে করত নিজেকে। একথা আমি কাউকে বলিনি, বাবা মা বন্ধু বান্ধবী কাউকে না, পাছে আমাকে সবাই অপবিত্র মনে করে। এবং আজও পাকা দাড়ি দেখলে আমার বমি আসে, আমি সব সময় তাদের ছোঁয়া বাঁচাতে ব্যস্ত থাকি, পাছে আশীর্বাদ করার ছলে ওরা আমার মনে আরও ঘৃণার জন্ম দেয়। মনে মনে ভাবি যেন আমার শুধু শাশুড়ি থাকে, কোনও ভদ্রবেশি শ্বশুর না থাকে। যখন বাসে চেপে কোথাও যাই, শুধুই খুঁজি একজন যুবককে, কোনও বৃদ্ধকে নয়। আমি লক্ষ্য করেছি যুবকেরা কিছুক্ষণ গল্প জমাবার চেষ্টা করে শেষে ক্ষান্ত দেয়, কিন্তু বুড়োরা কখনও ঘুমিয়ে, কখনও জেগে কেবলই শরীর চেপে বসে থাকে। আপনি সেইসব ছোট্ট কিশোরীদের নিয়েও কিছু লিখুন, যারা নিজেদের বাঁচাতে শেখেনি তথাকথিত দাদুদের কবল থেকে।’
চিঠিটি পড়ে মনে মনে ক্ষমা চাইলাম মৌ এর কাছে। বুড়োদের অথর্ব বলা আমার উচিত হয়নি। আসলে পুরুষ পুরুষই, সে খোকা হোক কি বুড়ো হোক। কয়লা ধুলে যেমন ময়লা ওঠে না, পুরুষের চরিত্রও তেমন, থুত্থুড়ে হলেও এটি শুদ্ধ হয় না।
এদেশে উত্তরাধিকার আইনগুলো করা হয়েছে ধর্মমতে। মুসলমানদের উত্তরাধিকারের বৈষম্য দেখে আমরা নিশ্চয় ভাবতে পারি মাতা ও পিতা সমান নয়। কন্যা ও পুত্র সমান নয়, স্ত্রী ও স্বামী সমান নয়। বৈষম্য আছে। কিন্তু বৈষম্য কেন? কেন মাতা কন্যা ও স্ত্রী পিতা পুত্র ও কন্যার সমান মর্যাদা পাবে না? এই বৈষম্য জলজ্যান্ত রেখে যে পুরুষ বা নারী ভাবে যে তারা তৃপ্ত,তারা সুখী, তারা সন্তুষ্ট তবে তারা নিজেরাই নিজের কবর খুঁড়ছে আর চতুর দর্শক দাঁড়িয়ে তালি দিয়ে তাদের অভিনন্দিত করছে। আমি চতুর নই বলে সম্পত্তি বন্টনের নমুনা দেখে আর সব পুরুষের মত সুখে ও স্বস্তিতে গা এলাতে পারছি না। আমি সমাজের ধিকৃত, বঞ্চিত, ধর্ষিত, নিরীহ, নিরূপায় নারী। উত্তরাধিকারের এই আইন আমি মানি না। সম্পত্তি বন্টনের সুস্থ আইন চাই। আজ থেকে চাই। এই মুহূর্ত থেকে। দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর গায়ে কি এই চরম বৈষম্যের কোনও ছ্যাঁকা লাগে না? আমার তো লাগে, তাঁর লাগে না কেন? তিনি যদি মানুষ হন, নারী হন, বিবেকবান হন, বুদ্ধিমান হন, তিনি যদি সৎ হন, নিষ্ঠ হন, এই অসম ব্যবস্থার চাবুক তাঁর হৃদয়ে পড়বেই।
লোকে বলে বাবার সম্পত্তি যদি কন্যা নেয়, তবে কন্যার তা সয় না। ও কেবল পুত্রের সয়। যেন সব সওয়ার কাজ শিশ্ন করে। শিশ্ন যাদের নেই, তাদের গায়ে সম্পত্তির কাঁটা ফোটে, সে মারা পড়ে। এইসব বলে কন্যাকে বিমুখ করতে চায় ধূর্ত লোকেরা। শেষ অবদি কন্যাকে বঞ্চিত করে তারা।
মাতৃকূলের চেয়ে পিতৃকুল বেশি লাভবান হয় সম্পত্তি ভোগের ক্ষেত্রে। ঠকাবার নিয়ম তৈরি করেছে শরিয়া বিধি। শরিয়া বিধির নখ দাঁত উত্তরাধিকারের শরীর কামড়ে ধরেছে।
নারী কখনও কোনও সম্পত্তিরঅংশীদার নয়। সে অবশিষ্টাংশভোগী। অবশিষ্টাংশভোগীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈধ উত্তরাধিকারী। অবশিষ্ট যা থাকে, তা পায়। বাড়ির পুরুষেরা খেয়ে দেয়ে যা থাকে, তা যেমন নারীরা খায়। তেমন সম্পত্তিও পুরুষ অংশীদাররা নিয়ে টিয়ে তলাঝাড়া যা থাকে, নারী পায়। স্ত্রী, কন্যা, মা, বোন, বৈপিত্রেয় বোন, সকলেই সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ পায়। কেউই অংশীদার নয়। কেউই প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী নয়। এই অবশিষ্টাংশ ভোগ করবার বেলায়ও সমাজের সাত রকম বাধা, বলা হয়, মেয়েরা সম্পত্তি নিলে সম্পত্তি সয় না।
সম্পত্তি সওয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। সয় না বলে সেগুলো পুরুষের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করা চলবে না। পিতার সমান মাতাকে, পুত্রের সমান কন্যাকে, স্বামীর সমান স্ত্রীকে সমান উত্তরাধিকার দেবার ব্যবস্থা করা হলে সব সইবে। আর তা না হলে যে সরকার আমাদের আইনের মাথা, তাঁকে কিন্তু আমরা বেশিদিন সইব না।
হিন্দুর উত্তরাধিকার আইনটি আরও ভয়াবহ। কোনও নারীর চিহ্ন নেই উত্তরাধিকার তালিকায়। নারী কিছু পাবার বেলায় নেই, কেবল দেবার বেলায় আছে। লোকে ভাবে, নারীর আর কী দরকার সম্পদ সম্পত্তির! তাকে পিতা স্বামী ও পুত্রের অধীনে বেঁচে থাকতে হয়। তাকে পরাশ্রয়ী লতার মত আঁকড়ে থাকতে হয় পুরুষের শরীর। নারীকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হতে দিতে সমাজ বড় নারাজ। সমাজ তাকে নিঃস্ব করেছে সর্বার্থে, তাকে অচল করেছে, অনাথ করেছে। হিন্দুরা এ দেশে আজও শাস্ত্র মতো চলে। মুসলমানরা খুব যে শাস্ত্রের বাইরে চলে তা কিন্তু নয়। . আসলে আইন কখনও হিন্দু মুসলমান বিচার করে হওয়া উচিত নয়। ধর্মের সঙ্গে সভ্যতার বিরোধ চিরকালীন। আইন যদি সভ্য না হয়, মানুষ সভ্য হবে না। আইনের হিন্দুত্ব আর মুসলমানিত্ব মানা অসভ্যতা ছাড়া কিছু নয়। মানুষকে সভ্য করতে হলে একটি আধুনিক সভ্য আইনের প্রয়োজন। আর এদেশের অসভ্য, অসংস্কৃত, অনাধুনিক, অধম মানুষদের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব কঠোর কঠিন আইন করা প্রয়োজন যে উত্তরাধিকার হোক, বিবাহ হোক, তালাক হোক, সন্তানের অধিকার হোক কোথাও নারী পুরুষে কোনও বৈষম্য থাকবে না। মানুষ হিসেবে সকলেই সমান হবে, সে বিশ্বাসে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ কি খ্রিস্টান হোক।
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমানের উত্তরাধিকার আইন নিয়ে আমার লেখাগুলো পড়ে অনেকে বলেছে আমি নাকি খুব কঠিন জিনিস নিয়ে লিখছি। কঠিন কেন জিজ্ঞেস করলে কিছু মেয়ে বলল এসব বুঝিটুঝি না। বললাম, তা বুঝবে কেন, বুঝলে কি আর সব পেয়েছির হাসি ঝোলে ঠোঁটে! এত তৃপ্ত থাকে হৃদয়! ওরা আমার তিরস্কারও বুঝল কি না জানি না তবে ওরা অনুরোধ করে গেল উত্তরাধিকারের কাঠখোট্টা আলোচনা বাদ দিয়ে পুরুষদের কি করে পেটানো যায় তা যেন লিখি। উত্তরাধিকারের ঝামেলায় কেউ যেতে চায় না। এটি ঝামেলা ছাড়া আর কী! গজ ফিতে নিয়ে শতাংশ মাপা, আর নিজের ভাইদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করা ঠিক শোভন মনে হয় না। আপন ভাই ই তো, না হয় নিলই সব। আর বাপের বাড়ির জমি, এটির ভাগ চাইলে লোকে লোভী ভাববে। বাপ তো বিয়ের আগ অবধি খাওয়ালো পরালো, এখন স্বামী খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, অসুবিধে তো কিছুতে নেই। খামোকা অসভ্যের মত বাপের দুকানি জমির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে কেন! এই হল আমাদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নারীদের মানসিকতা। আর নিম্নবিত্তের তো জমিই নেই, যদিও বা থাকে তার ভাগ চাইতে এলে ভাইয়েরা ঠেঙিয়ে বিদেয় করে। কিন্তু এই ঘটনাগুলো আর কদিন ঘটবে? কদিন আমাদের নিরীহ, নির্বোধ, প্রতারিত মেয়েরা ভাববে যে পিতার সম্পত্তি কেবল পুত্রদের জন্য, কন্যাদের জন্য নয়, আর কন্যাদের জন্য হলেও তা ছিটেফোঁটা। কবে তাদের বোধ হবে যে পিতার সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমান অধিকার থাকা উচিত! কারণ কন্যা একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ, সে পুত্রের তুলনায় কিছু কম সন্তান নয়, কিছু কম মূল্যবান নয়, কিছু কম মেধাবী নয়। এই বোধ যখন হবে তখন সে নিজে উত্তরাধিকার আইনের মা বাপের হাতে গজফিতে দেবে এবং বলবে আমার যা কিছু প্রাপ্য তার সবই দাও, আমি কড়ায় গণ্ডায় সব হিসেব চাই। আমি এই জগতে একে ওকে দান দক্ষিণা করতে আসিনি। আমার যা, আমি তা একশ ভাগ চাই। আর পুত্র তৈরিতে একটি শুক্রাণু আর ডিম্বাণু যেখানে লাগে, কন্যা তৈরিতে সেখানে আধা শুক্রাণু বা আধা ডিম্বাণু লাগে না। তবে সম্পত্তির বেলায় আধা কেন! পুরুষ প্রগতিবাদীরা নানারকম আন্দোলন করে। কিন্তু উত্তরাধিকার আইন নিয়ে তারা কখনও রা শব্দ করে না। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি তাদের একদম অপছন্দ। আমি অনেক বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিককে জানি যারা মেপে মেপে জমি নিয়েছে বোনদের অর্ধেক দিয়ে অর্থাৎ ঠকিয়ে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনও হেরফের দেখলে তারা উত্তেজিত হন, কিন্তু জমি বন্টনে কোনও হেরফের বা বৈষম্য দেখলে তারা খুব শান্ত থাকেন, মোটেও উত্তেজিত হন না। যেন শরিয়ত মত আর কিছু না চলুক, উত্তরাধিকার আইন চলছে চলুক। বিয়ের ব্যবস্থাও চলুক। যেহেতু বহুবিবাহের সুবিধাদি আছে।
যা করবার তা নারীকেই করতে হবে। নারীর জন্য সুযোগ সুবিধা তৈরি করতে হবে নারীকেই। প্রতিবন্ধক সরাতে হবে তাকেই, তার পথ মসৃণ করবার দায়িত্ব তারই। আমাদের সমাজে সহজেই গোলাম আযম জন্মায়, ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর জন্মায় না। তাই বহুবিবাহও দূর হয় না। সম্পত্তির সমান অধিকারও জোটে না। মেয়েদেরই তাই এক একজন প্রীতিলতা, লীলা নাগ, বেগম রোকেয়া হতে হবে। মেয়েদের জলের মত হৃদয় শত বারুদে এবার দাউ দাউ জ্বলে ওঠা প্রয়োজন।
নতুন একটি কথা উঠছে যে পুরুষের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ বিবাহ করতে হলে আদালতের অনুমতি লাগবে। আগে স্ত্রীর অনুমতি লাগত আর এখন আদালত থেকে অনুমতি নিতে হবে। এতে নারীর কী লাভ হল শুনি! পুরুষের জন্য কি আদালত থেকে অনুমতি নেওয়া খুব দুরূহ কোনও কাজ যে এ কাজে তারা ভয় পাবে! আদালতও দুর্লভ নয়, আদালতের অনুমতিও দুর্লভ নয় এদেশে। কথা যখন উঠেছেই, পুরুষের শখের বহু বিবাহ বন্ধ করবার কথা কেন ওঠে না! নাকি সাহস হয় না! পুরুষকে খানিকটা খুশি করে বিল পাশ না করলে বুঝি চলে না? যদি বিল পাশ করতেই হয়, তবে অনুমতির ফাজলামো বাদ দিয়ে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করবার বিলই পাশ করতে হবে। এইসব খুচরো সংশোধন আমরা মানব না, আমূল সংশোধন চাই। আমূল বদল চাই এই ঘুণে ধরা সমাজের। সভ্য আইন চাই, মানুষের আইন চাই; ধর্মের নয়, অসত্যের নয়, অপমানের আইন আর নয়। ভাতের ক্ষিধেকে একমুঠ মুড়ি মুড়কি দিয়ে মেটাতে চাইলে আমরা অনশন করব বলে দিচ্ছি। অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার দিন চলে গেছে, এবার প্রাপ্যটুকু চাই, এবার অধিকার সবটুকু চাই।
এই পৃথিবীতে এককালে পুরুষেরা নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য লোহার বেড়ি বানিয়েছিল। এই পুরুষেরা নারীর সতীত্ব প্রমাণ করবার জন্য নারীকে মরা স্বামীর চিতায় তুলেছে। এই পুরুষেরা এখনও বীভৎস সব পন্থায় নারীর সতীত্ব রক্ষা করে চলেছে। নানা নিয়ম কানুন নারীর ওপর চাপিয়ে নারীর সতীত্বের মজা তারা উপভোগ করছে। আগে লোহার বর্ম ব্যবহার করা হত, এখন সামাজিক অঙ্গুলী নির্দেশেই কাজ হয়। সমাজ নারীকে বলছে ঘরে থাকো, স্বামীর আদেশ ছাড়া ঘর-বার হয়ো না, পুরপুরুষের সঙ্গে মেশো না, মিশলে তালাক, মিশলে মরণ। .. নারীর দেহে গায়ে তালা লাগিয়ে চাবিটি কোনও পুরুষের নেবার অধিকার নেই, নারীর দেহের চাবি নারীর কাছেই থাকতে হবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেমন নারীর প্রয়োজন, যৌন স্বাধীনতাও নারীর প্রয়োজন, যৌন স্বাধীনতা না থাকলে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক যত স্বাধীনতাই নারীর থাকুক, সত্যিকার স্বাধীন সে নয়। নারীর যৌন স্বাধীনতার কথা শুনলে অনেকে নাক সিটকোবে, বলবে, ছিঃ ছিঃ নারীর আবার যৌন স্বাধীনতা কী? তাহলে তো সে বেশ্যা হয়ে গেল। নারীর সবটুকু স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সমাজ যদি তাকে বেশ্যা বলে, তবু বেশ্যা হওয়া ভাল পুরুষের দাসি হওয়ার চেয়ে। আসলে যৌন স্বাধীনতা নারীর আর সব স্বাধীনতার মত একটি স্বাধীনতা। নারী যে কোনও স্বাধীনতা পেলেই তাকে বেশ্যা বা নষ্ট বলা হবে এই ভয় দেখানো হয়। এসব পৌরুষিক চক্রান্ত ছুঁড়ে ফেলে নারীকে যদি মানুষ হতে হয়, তার শরীর ও মনের সবটুকু স্বাধীনতা তাকে অর্জন করতেই হবে।
কথায় কথায় ইনশআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সোবহানআল্লাহ বলার চল শুরু হয়েছে। বুদ্ধি হবার পর থেকে এই শব্দগুলো কখনও উচ্চারণ করিনি আমি। আসসালামু আলায়কুম বলে কাউকে আমি সম্ভাষণ জানাই না, খোদা হাফেজও বলি না বিদায় নেবার সময়। এসব বিদেশি শব্দের পরিবর্তে আমি বাংলা শব্দ ব্যবহার করি। আল্লাহ খোদার নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে আজকাল। এতে আল্লাহর কোনও মঙ্গল হয় না। মঙ্গল হয় না তাদেরও, যারা বলে। আসলে সৎ হতে হয়, বিবেকবান হতে হয়, উদার, সহনশীল, যুক্তিবাদী হতে হয়, তবেই সত্যিকার মঙ্গল হয় মানুষের আর মানুষের মঙ্গল মানে মানবজাতির মঙ্গল।
যারা এই রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে, তাদের ধিককার দিই আমি। ধর্মহীনতা গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত। এই শর্ত পূরণ না হলে গণতন্ত্রের নাম ধারণ করবার অর্থ জাতিকে বোকা বানানো। স্বৈরাচারের একটা সীমা আছে। এই সরকার সেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এক স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে নব্বইএ যে গণ জাগরণ হয়েছিল, তেমন একটি জাগরণের প্রয়োজন এখন। একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের জন্য আমাদের সবার এখন পথে নামা জরুরি। পঙ্গপাল যেমন শস্য নষ্ট করে, মাওলানারা তেমন সোনার বাংলার গ্রামগুলো নষ্ট করে ফেলছে। তাদের যদি এখনও নির্মূল করা না হয় তবে একদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে গোটা বাংলাদেশ। তখন হাহাকার করে লাভ কিছু হবে না। তাই এখনই সতর্ক হতে হবে সবার।
ফতোয়াবাজেরা গ্রামে গ্রামে মেয়েদের, যে মেয়েরা স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছে, ফতোয়া দিয়ে সমাজচ্যুত করছে। সারাদেশে যত ফতোয়াবাজ মাওলানা আছে তাদের সমাজচ্যূত করার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করুক নতুন প্রজন্ম। ফতোয়াবাজরা একদিন নির্মূল হবে এই বিশ্বাস আছে বলেই এখনও সম্ভবত বেঁচে আছি এবং এখনও এই দেশ নিয়ে গৌরব করি।
আমাদের প্রগতিবাদীরা বলেন, মৌলবাদ গেলেই সব সমস্যা ঘুচবে। তাঁরা এও বলেন, ধর্ম নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, মানুষ নীরবে নির্ভতে ধর্ম পালন করুক, রাষ্ট্রধর্মেও ইসলামটা বহাল থাকুক, কিন্তু দেশ থেকে যে করেই হোক মৌলবাদটা দূর করতে হবে। তাঁদের এই কথা আমি মানি না। আমি মনে করি, ধর্ম যতদিন থাকবে, মৌলবাদ থাকবেই। ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে ঘরের লোককে যদি কেউ সান্ত্বনা দেয় যে সাপকে বুঝিয়েছে সাপ ছোবল দেবে না সে কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? সাপ আজ ছোবল দিচ্ছে না, কাল দেবে। সাপকে বুঝিয়ে শান্ত করার কিছু নেই। সাপের কাজই ছোবল দেওয়া। বিষবৃক্ষ শরীরে বাড়ছে বলে ডাল পালা কেটে দিলে বৃক্ষ কি ডাল ছড়াবে না আর? বিষ ফলাবে না তার শত শাখায় পাতায়? ফলাবে। সুতরাং আমরা আশা করতে পারি না মৌলবাদ নামক বৃক্ষটি কেটে দিয়ে মৌলবাদ ঘোচাতে পারব। মৌলবাদের শেকড় যতদিন আছে, ততদিন মৌলবাদ গজাবেই। মৌলবাদের শেকড়টির নাম ধর্ম। যদি মৌলবাদ নির্মূল করতে গিয়ে মৌলবাদের শেকড়টি উপড়ে না ফেলি, তবে মৌলবাদ কোনওদিনই নির্মূল হবে না।’
ইদানীং বড় মামা প্রায়ই আসেন আমার বাড়িতে। সোভিয়েত দূতাবাসের চাকরিটি বড় মামার গেছে। অনেকদিন ভোরের কাগজ পত্রিকার আন্তর্জাতিক পাতাটি দেখার দায়িত্বে ছিলেন। এখন সেই দায়িত্বটিও নেই। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি যেভাবে বড় মামা ব্যাখ্যা করতে চান, পত্রিকার অন্যরা সেভাবে চান না। মার্কসবাদে বিশ্বাসী কট্টর কমিউনিস্টএর মতের সঙ্গে কাগজের লোকদের মত মেলে না। বড়মামা অনেকটা ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকের মত এখন। বেশির ভাগ লেখাই তিনি ছদ্মনামে লেখেন। আমার লেখার ঘরে একদিন তিনি একটি বই দেখেন, ব্ইয়ের নাম তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা। বইটির লেখক দুজন ইসলাম-বিশেষজ্ঞ। বইয়ের পেছনের পঈচ্ছদে বড় বড় করে মুসলমান হয়ে আল্লাহ এবং রসুলের নিন্দা করলে যে শাস্তির বিধানটি আছে সেটির বর্ণনা, পেছন দিক থেকে তলোয়ার দিয়ে অপরাধীর ডান হাত এবং বাঁ পা কেটে নিতে হবে, তারপর বাঁ হাত আর ডান পা। বড়মামা বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই আগ্রহ প্রকাশ করলেন পুরো বইটি পড়ার। বইটি একদিন নিয়ে যান তিনি, যখন ফেরত দিতে আসেন, সঙ্গে একটি দৈনিক সংবাদ পত্রিকা আনেন, যে পত্রিকায় ছাপা হয়েছে বড়মামার নিজের নামে লেখা বইটির সমালোচনা। বড়মামা নিজে ইসলামের পণ্ডিত। ইসলাম ব্যবহার করেই তিনি আক্রমণ করেছেন ইসলাম বিশেষজ্ঞদের, কেবল ইসলাম বিশেষজ্ঞদের নয়, সব ধরনের ধার্মিকদের, যারা কুরআন হাদিস মাথায় তুলে রাখছেন কিন্তু নিজেরা কুরআন হাদিসের আদেশ মেনে চলছেন না। বড়মামা দেশের রাজনৈতিক নেতা আর উপনেতাদের প্রসঙ্গে লিখেছেন যে তাঁরা প্রায়ই বলেন, ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান, ধর্মীয় জলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে গিয়ে তাঁরা জনগণকে কুরআন হাদিস অনুসরণ করে চলার উপদেশ দেন কিন্তু তাঁদের দৈনন্দিন চালচলনে, চিন্তাভাবনায় ও কাজকর্মে তার প্রমাণ তাঁরা দিচ্ছেন না। এমনিতে সার্ট প্যান্ট পরছেন অর্থাৎ বিধর্মীদের পোশাক পরছেন কিন্তু ইসলামি জলসায় গেলে তড়িঘড়ি ইসলামি পোশাক পরে নিচ্ছেন, মাথায় একটি টুপিও পরে নিচ্ছেন, কিন্তু গালটি কামানো। কেন গো! বুখারি হাদিস আর মুসলিম হাদিসে তো স্পষ্ট লেখাই আছে ‘দাড়ি রাখা ওয়াজিব আর কেটে ফেলা হারাম।’ তবে হারাম কাজটি করছেন কেন তাঁরা, এতই যদি ইসলাম পছন্দ তাঁদের!
‘রাষ্ট্রীয় পদাধিকার বলে তাঁরা আবার অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানেও প্রধান অতিথি হিসেবে গিয়ে সেই ধর্মের প্রশংসা করেন। অথচ কুরআন হাদিস অনুসারে ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মই বাতিল ও কুফর। অন্য ধর্মের প্রতি দয়া দেখানোর জন্য কিংবা অন্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া কি ইসলাম অনুসারে বৈধ? কুরআন ও হাদিস তো বলে ‘যারা যায় তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের সাথেই তাদের হাশর কবে।’ কুরআনে আল্লাহ নিজে মুমিনদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘মুহম্মদ আল্লাহর রসুল, যারা তাঁর সঙ্গে রয়েছে তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর, এবং নিজেদের মধ্যে পরষ্পরের প্রতি দয়াশীল(৪৮.২৯)ঞ্চ, অন্য আয়াতে বলেছেন, ‘তারা মুমিনদের প্রতি কোমল, কাফিরদের প্রতি কঠোর(৫.৫৪)’, আরও বলেছেন, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না (৪.১৪৪)। সমালোচকরা এ ব্যপারে নীরব কেন?’
বইটির এক জায়গায় লেখা, ‘তসলিমা নাসরিন নামাজ বলে যে শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন তা একটি ফার্সি শব্দ। সমগ্র কুরআন মজিদ ও হাদিস শরীফে এ ধরনের কোনও শব্দ নেই। আল কুরআন ও হাদিসে যে শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে সালাত। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) মিরাজের পর থেকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন।’ বড়মামা এর উত্তরে লিখেছেন, ‘খুবই সত্য কথাটি বলেছেন সমালোচক। নামাজ অবশ্যই একটি বিদেশী, বিজাতীয় উদ্ভট ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী শব্দ। সালাত শব্দটির বদলে নামাজ শব্দটি ব্যবহার না করে মাঝে মাঝে কুরআন শব্দটি ব্যবহার করলেও অশুদ্ধ হত না, কারণ কুরআন মজিদে সালাত অর্থে একটি আয়াতে দুই দুই বার কুরআন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, ফজরের সালাত বোঝাতে ফজরের কুরআন বলা হয়েছে ১৭ নং সুরার ৭৮ নং আয়াতে। কিন্তু বিজ্ঞ সমালোচকরা এতদিন কোথায় ছিলেন? হাজার বছর ধরে উপমহাদেশে, ইরান, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার মুসলমানরা তসলিমার মত ভুল করে সালাতকে নামাজ বলে আসছে, নামাজ শিক্ষা বই সহ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে লাখ লাখ বই পুস্তকে নামাজ শব্দ ব্যবহার হচ্ছে। টেলিভিশন ও রেডিওতে আজানের দোয়ায় প্রতিদিন কয়েকবার করে বলছে এই নামাজের তুমিই প্রভু, সাওমকে সাওম না বলে রোজা বলা হয় কেন? রোজা শব্দটি তো কুরআন বা হাদিসের কোথাও নেই। তাছাড়া কুলখানি, চেহলাম, ফাতেহায়ে দোয়াজদহম, ফাতেহাায়ে ইয়াজদহম, আখেরী চাহারশুম্বা ইত্যাদি কোথায় পেলেন? মুসলমান শব্দটিই কি কুরআন বা হাদিসে আছে? মুসলমান শব্দটি মুসলিম শব্দের বিকৃতি। মুসলিম শব্দটির অর্থ আত্মসমর্পিত, অনুগত, কিন্তু মুসলমান শব্দের অর্থ কি?’
বইটিতে এম এন রায়, এ জি আরবেরি, আর ও নিকলসন, ডঃ মরিস বুকাইলির খুব প্রশংসা করা হয়েছে, ওঁদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, এবং আমাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে ওঁদের বই যেন আমি পড়ি। বড়মামার মন্তব্য, ‘ইসলামের প্রশংসা করার পরও ওঁরা যে ইসলাম গ্রহণ না করে কাফেরই রয়ে গেছেন, বরং কথায় এক কাজে আরেক নীতি অবলম্বন করে ওঁরা যে দারুণ মুনাফেকিও করলেন, এ কথাটি তসলিমার বিজ্ঞ সমালোচকরা বেমালুম চেপে গেছেন।’
বইটিতে লেখা যে আমি আমার বইয়ে কিছু হাদিসের উল্লেখ করেছি কিন্তু হাদিসের রেফারেন্স দিইনি। এসব হাদিস সহি না জাল তার উল্লেখ করিনি। এসব কারণে আমার উদ্ধৃত হাদিস সম্পর্কে তাঁদের আলোচনা করা সম্ভব হল না। আরও লিখেছেন, হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে তেমন কোনও জ্ঞান আমার নেই। বড়মামা এর উত্তর দিয়েছেন এভাবে, ‘কিন্তু দুই ইসলাম বিশারদের যদি হাদিস সম্পর্কে কোনও জ্ঞান থাকত, তাহলে তসলিমার উল্লেখ করা কোন হাদিসগুলো জাল বা বানোয়াট হাদিস তা তাঁরা ধরতে পারতেন।’
আমি যখন বইটি পড়ি, এই ছোটখাটো ব্যপারগুলো আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু বড়মামার নজর খুব কড়া। লিখেছেন —হাদিসের সূত্র উল্লেখ না করা যদি তসলিমার অ্যাকাডেমিক ডিসঅনেস্টি হয়, তবে বাংলাদেশের রেডিও টেলিভিশনে যে প্রতিদিন সনদ বা উৎস উল্লেখ ছাড়াই হাদিস সম্প্রচার করে যাচ্ছে, এই সমালোচকরা কি তার কখনও প্রতিবাদ করেছেন? প্রচার মাধ্যমে কেবল হাদিস নয়, কুরআনের বহু গুরুত্বপূর্ণ আয়াতকে পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত ব্ল্যাকআউট করে আসা হচ্ছে তারও কি কোনওদিন প্রতিবাদ করেছেন? রেডিও টিভিতে সাধারণ মানুষের কি করতে হবে না করতে হবে সে সম্পর্কিত আয়াতগুলো পুনঃ পুনঃ প্রচার করা হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদের, আইনপ্রণেতাদের, শাসক এবং বিচারকদের কি করতে হবে না হবে সে সম্পর্কিত আয়াতগুলো প্রচার করা হয় না। যেমন, ‘চোর ও চোরণীর হাত কেটে ফেলো (৫.৩৮)’, ‘ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের দুজনের প্রত্যেককে একশটি চাবুক মারবে, আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে গিয়ে তাদের দুজনের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও, আর মুমিনদের একটি দল যেন ওদের দুজনের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে (২৮.২)ঞ্চ, ‘আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তদনুযায়ী যারা হুকুম না করে তারা কাফির (৫.৪৪)ঞ্চ প্রভৃতি অনেক আয়াত কোনওদিন প্রচারিত হতে দেখি না এবং বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও সমাজে আল্লাহর এসব বিধান কার্যকর করতেও দেখি না। এ সম্পর্কে অবশ্য আল্লাহ আগে থেকেই বলে রেখেছেন, ‘আমি যেসব স্পষ্ট বিধান ও পথনির্দেশ নাজিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবে, তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে লানত (অভিশাপ) দেন, এবং লানতকারীরাও তাদেরকে লানত দেয় (২.১৫১)।’
বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে বড়মামা কেবল বইয়ের লেখকদের যুক্তি খণ্ডন করে এবং তাদের প্রশ্নের উত্তরে কঠিন প্রশ্ন করে ক্ষান্ত হননি। আজকের যুগে ধর্ম মানছি, কিন্তু আমি মৌলবাদী নই বলে অধিকাংশ মানুষ যে নিজেদের বেশ আধুনিক বলে দাবি করছে এবং কোরান থেকে ভাল ভাল কিছু বাক্যের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ যে কত ভাল কথা বলেছেন তার উদাহরণ দিচ্ছেন, তাদের উদ্দেশেও বেশ যুক্তিপূর্ণ কথা লিখেছেন বড়মামা। লিখেছেন, ‘কুরআনের কিছু কিছু অংশে বিশ্বাস করলে, মেনে চলতে বললে আজকাল কেউ মৌলবাদী হয় না, কিন্তু এই একই কুরআনের অপর কিছু অংশে বিশ্বাস করলে, মেনে চলতে ও কার্যকর করতে বললে সে মৌলবাদী হয়ে যায় এবং ইসলামের কোনও কোনও স্বঘোষিত রক্ষক আবার মৌলবাদী হতে রাজি নন, লজ্জা পান। অথচ ইসলামের ভেতর ভেজাল, নকল ও বিদআত আমদানি, প্রবর্তন ও লালন পালন করতে লজ্জা পান না, কারণ ওসব করলে কেউ মৌলবাদী বলবে না। কিন্তু কুরআনেই বলা হয়েছে, কুরআনের সমস্ত অংশই মানতে হবে। বলা হয়েছে, ‘তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে(২.৮৫)।’ কুরআনের কোনও একটি অংশকে তুচ্ছ করা বা না মানা পুরোটাই তুচ্ছ করা ও না মানারই সামিল। কুরআনেই এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘এরাই তারা যারা তাদের আচরণ ও কাজকর্মের মাধ্যমে বলতে চায় আমরা কতক অংশে বিশ্বাস করি ও কতককে প্রত্যাখ্যান করি, এবং চায় মধ্যবর্তী কোনও পথ অবলম্বন করতে। প্রকৃতপক্ষে তারাই কাফির (৪.১৫০,৪.১৫১)।’
বড়মামার বক্তব্য যে কোনও মৌলবাদীরই পছন্দ হবে। কিন্তু বড়মামার উদ্দেশ্য মৌলবাদিদের খুশি করা নয়, যারা ধর্মেও আছে জিরাফেও আছে মূলত তাদের অখুশি করা। আজকের কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ যেভাবে ধর্মের গুণগান গাইছেন এবং ধর্মীয় সন্ত্রাসের জন্য দোষ দিচ্ছেন মৌলবাদীদের, তাদের জন্যই লেখা এটি। তাঁরা আমার এবং বড়মামার দুজনেরই বিশ্বাস মৌলবাদীদের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর, বেশি ভয়ংকর। ‘মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে কুরআন তো অভ্রান্ত, অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে হুবুহু আছে এবং চিরদিন থাকবে, কুরআন অপরিবর্তনীয়, এর সুস্পষ্ট বিধানগুলো অপরিবর্তনীয়। কুরআনের কিছু কিছু অংশ ব্ল্যাক আউট করলে কিংবা কুরআনে আল্লাহর দেয়া স্পষ্ট আইনগুলোর বদলে পাশ্চাত্যের দেয়া আধুনিক আইনের মাধ্যমে কেউ শাসন ও বিচার কাজ চালালে সে যে মুসলিম নয় এটাতো কুরআনেরই কথা। কুরআনই তো বলে, সে কাফির(৫.৪৪), জালিম (৫.৪৫) এবং ফাসিক(৫.৪৭)।’
লেখাটি শেষ করেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে, ‘পাকিস্তান আমলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৪ বছর এবং বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেয়ার পর ১৯৭৫ থেকে এ যাবৎ ১৮ বছর নিয়ে মোট ৪২ বছরে ইসলামি বিধান চালু না করে শুধু বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আর রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এর নামে মুসলমানদের চোখে ধুলো দেওয়া হয়েছে। ইসলামি আইন ও ইসলামি বিধানের কথা যারা বলে তাদেরকে মৌলবাদী খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এরশাদের শাসনকালে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিল পাসের সময় সংসদে সমাপনী ভাষণে তখনকার প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মৌলবাদকে ঠেকানোর জন্য এই বিল আনা হয়েছে। এরা কি মুমিন মুসলিম না কি মুসলিম নামধারী আধুনিক পশ্চিমা ভাবধারার অনুসারী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ, স্যার মোহাম্মদ ইকবাল প্রমুখের ভাবশিষ্য? তবে আর যাই হোক, এই আধুানতাকাবাদী ধর্মব্যবসায়ীরা মৌলবাদের আগা কেটে গোড়ায় পানি ঢালছেন, ফলে মৌলবাদের গাছটি কিন্তু ক্রমেই তরতাজা হয়েই বাড়ছে।’
বড়মামার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তিনি নাস্তিক এ কথা আমি জানতাম, কিন্তু তাঁর আক্রমণ যে ধর্ম দিয়েই বকধার্মিকদের এমন আচ্ছ! করে পেটানো এবং হাতিয়ারটি যে বড়মামার এত ধারালো তা আমার জানা ছিল না। বড়মামার সঙ্গে আগে কখনও আমার ধর্ম নিয়ে কোনও বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। ইদানীং আমার লেখা পড়ে বড়মামারও আগ্রহ জন্মেছে, বড়মামার লেখা পড়ে আমারও। বাড়িতে এলেই সোজা আমার লেখার ঘরে ঢুকে যান বড়মামা। কোরানের নারী নতুন একটি বই লিখছি আমি, কোরানে নারী সম্পর্কে যে সব আয়াত আছে, সেসবের উল্লেখ করে সেসব বিষয়ে মন্তব্য কেবল। লেখাটি, যেহেতু আরবি জানেন ভাল, তাঁকে দেখাই। কোরান বড়মামার নখদর্পনে। তিনি মুখস্ত আওড়ে যান কোরানের আয়াত এবং আয়াতের ব্যখ্যা। কোরানের প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে অনুবাদ করেন। আমার পাণ্ডুলিপিতে চোখ বুলিয়ে বড়মামা কয়েকটি ভুল খুঁজে পেয়েছেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বাংলা কোরান অনুবাদ, কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা ইসলামি ফাউণ্ডেশন ট্রাস্টের কোরান, মাওলানা মওদুদির অনুবাদ সব তুলনা করে মিলিয়ে আমি আরবির অনুবাদ উদ্ধার করেছি, কিন্তু এই উদ্ধারের পরও আরও উদ্ধার করা যায় যদি ভাষাটি জানা থাকে ভাল। বড়মামা ভাষাটি জানেন বলে তিনি কোন আরবি শব্দকে ভাবান্তর করে কোন অনুবাদক কোনও একটি মোলায়েম অর্থ দাঁড় করিয়েছেন কোনও আয়াতের, সেগুলোও ধরে ফেলতে পারেন। মেয়েদের যখন মারবে তখন খুব আস্তে করে মারবে, মুখমণ্ডলে মেরো না — এরকম একটি অনুবাদ পড়ে বড়মামা হেসে বললেন, কোরানে আস্তে করে মারার কথা লেখা নেই, আস্তে করে শব্দদুটি অনুবাদক যোগ করেছে। যত পুরোনোকালের বাংলা কোরান পাওয়া যায়, তত সঠিক অনুবাদও পাওয়া যায়। দিন যত যাচ্ছে, যত আধনিক হচ্ছে সমাজ, মেয়েদের অধিকারের কথা উঠছে, ইসলামে নারীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এই দাবি করছেন ইসলামি পণ্ডিতরা, এই পণ্ডিতরাই কোরান অনুবাদের সময় নিজে থেকে আল্লাহর নিষ্ঠুরতা আড়াল করার দায়িত্ব নিয়েছেন। যেন আল্লাহ যদি আস্তে করে মারার কথা বলেন, আল্লাহকে খুব দরদী মনে হবে। আরবি ভাষাটি না জানলে আজকালকাল পণ্ডিতের আল্লাহর ওপর নাপতানিগুলো আবিস্কার করা যায় না। কোথাও কোন আয়াতের বাংলা অনুবাদে ভুল আছে কি না তা আরও সুক্ষ্ণভাবে দেখে দিতে বড়মামা আমার পুরো পাণ্ডুলিপি তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। কয়েকদিন পর কিছু কিছু শব্দের ভুল শুদ্ধ করে নিয়ে আসেন। পাণ্ডুলিপি হাতে নিতেই বুঝি তিনি বেশ পরিশ্রম করেছেন এর পেছনে।
শয়তানের আয়াত নিয়ে কথা হতে থাকে বড় মামার সঙ্গে। সুরা আল নাজলএর একুশ আর বাইশ নম্বর আয়াত দুটো কোরান থেকে উড়িয়ে দিয়ে নতুন আয়াত বসানো হয়েছে। কারণ মোহাম্মদ যে আয়াত উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলো তিনি পরে বলেছেন যে শয়তানের ছিল। মোহাম্মদের কানে কানে শয়তান উচ্চারণ করেছে আয়াত দুটো। মোহাম্মদ বুঝতে পারেননি কোন কণ্ঠস্বরটি আল্লাহর, কোনটি শয়তানের, অথবা তাঁর জিভে ভর করেছিল শয়তান, অথবা মাথায়, তাই কাবা শরীফের সামনে বসে তিনি উচ্চারণ করলেন..। কী উচ্চারণ করলেন, বড় মামাকে জিজ্ঞেস করি। বললেন, ‘তোমরা কি আল লাত, আল উযযা আর তিন নম্বর আল মানাতএর ব্যপারে চিন্তা ভাবনা করিয়াছো?’
‘এই টা কোরানে আছে, কিন্তু কোনটা বাদ দেওয়া হইছে?’
‘দিজ আর ইন্টারমিডিয়ারিস এক্সলটেড হুজ ইন্টারসেশন ইজ টু বি হোপড ফর। এইটা তো একুশ নম্বর, আর বাইশ নম্বরটা হচ্ছে, সাচ এস দে ডু নট ফরগেট। —এই আয়াত দুইটা পরে শয়তানের আয়াত বইলা বাদ দিয়া লেখা হইছে, আর ইওরস দ্যা মেইলস এণ্ড হিজ দ্যা ফিমেইলস? তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যা? এটা তো তবে প্রতারণা পূর্ণ বণ্টন!’
আমি জিভ কাটি লজ্জায়।
বড় মামা বলেন, ‘লাত, উযযা আর মানাত কে কোরাইশ বংশের লোকেরা আল্লাহর তিন কন্যা বলে বিশ্বাস করত। ওদের গডএর নাম তো আল্লাহ। আল্লাহ নামটা তো মোহাম্মদ ওদের কাছ থেকেই নিয়েছে, মানে মূর্তি পূজা যারা করত, যারা বহুঈশ্বরবাদী ছিল তাদের কাছ থেকে।’
‘মোহাম্মদের উদ্দেশ্যটা কী ছিল আল্লাহর তিন মেয়েরে সম্মান দেখানোর?’ প্রশ্ন করি।
বড় মামা বলেন, ‘সেই সময় মানে সেই আটশ খ্রিস্টাব্দে যে ইসলামিক স্কলাররা মোহাম্মদের জীবনী লিখে গেছে, ইবনে জারির আল তাবারি, আল ওয়াহিদি, ইবনে সাদ, ইবনে ইসাক, তাদের ভাষ্য, যে, ওই সময় মককায় মোহাম্মদের তেমন কোনও অনুসারী ছিল না, যারা ছিল তাদের বেশির ভাগই মোহাম্মদকে ছেড়ে চলে গেছে। তখন কোরাইশদের দলে টানার জন্য সে তাদের তিন দেবীর কাছে মাথা নোয়াইছে। মোহাম্মদ এইটা বলার পর কোরাইশরা খুশি ছিল তার ওপর।..’
‘আয়াতটা পাল্টাইল কখন?’
এমন সময় মা মা ঢোকেন ঘরে। আমরা চুপ হয়ে যাই। মা দুজনের মুখে চেয়ে জিজ্ঞেস করেন, ‘কী আলাপ করতাছ তোমরা?’
বড় মামা সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, ‘এই তো ওর পিজিতে পড়ার কথা বলতেছি! পড়লে তো মেডিকেল কলেজের প্রফেসার হইতে পারতো!’
মার মুখটি মুহূর্তে প্রসন্ন হয়ে ওঠে, ‘চা খাইবা মেবাই?’
‘হ। এক কাপ চা দে।’
মা চা করতে চলে গেলেন।
ঘরে আবার শয়তানের আয়াত নিয়ে কথা চলতে থাকে।
‘সুরা হজ্জের বায়ান্ন আর তিপ্পান্ন আয়াতে তো আছে এই শয়তানের কথা। মোহাম্মদকে আল্লাহ বলতেছে, যে, আল্লাহ যত নবী রসুল পাঠাইছিল মোহাম্মদের আগে, সবাইরেই নাকি শয়তানে ধরছিল।’
হঠাৎ মার মুখটি দরজায়।
‘মেবাই তোমরা কী নিয়া কথা বলতাছ?’
আমি বলি, ‘না কিছু না, এমনি।’
‘আমি শুনলাম আল্লাহ মোহাম্মদ!’ বড়মামার দিকে তাকিয়ে মা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, ‘তুমি নাসরিনরে কী শিখাইতাছ?’
বড় মামা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান ঘর থেকে, আমি পেছন পেছন যাই বলতে বলতে ‘আমারে আবার কি শিখাবে? এমনি আলাপ করতাছিলাম।’
‘মেবাই, কী নিয়া আলাপ করতাছিলা তুমরা? কী বুদ্ধি দিতাছ আমার মেয়েরে?’ মা আগুন-চোখে তাকান বড়মামার দিকে। বড়মামা মার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে দেয়ালের চিত্রকর্মে, জানালার পর্দায়, দরজার হাতলে ফেলে রাখেন।
মার গলা চড়তে থাকে। ‘এত বড় সর্বনাশ করতাছ তুমি মেয়েটার? জানতাছ তো কী হইতাছে দেশে। অত বড় বড় মিছিল যায়, দেখতাছ না? পত্রিকায় পড়তাছ না কি হইতাছে? তারপরও তুমি ওরে আল্লাহর বিরুদ্ধে লেখার পরামর্শ দেও? মেয়েডা বাইচা থাকুক তা চাও না? যে কোনওদিন তো ওরে মাইরা ফেলবে! নিজে যা বিশ্বাস কর, কর। আমার মেয়েরে তুমি নষ্ট বানাইও না। ওরে কুবুদ্ধি দিয়া যাও, আর ও এইসব লেখে। তুমি ওরে কুবুদ্ধি দিয়া দিয়া কোরানের বিরুদ্ধে, আল্লাহর বিরুদ্ধে লেখাইছ।’
আমি বলি, ‘আমি নষ্ট হইয়াই রইছি। আমারে নতুন কইরা নষ্ট বানানির কিছু নাই।’
বড়মামা মলিন মুখে বলেন, ‘আমি তো আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ কথা কই নাই। যারা আল্লাহ নিয়া ব্যবসা করে, তারা কয় খারাপ কথা। তারা আল্লাহরে অসৎ কাজে ব্যবহার করে।’
সেদিন বড়মামার চা খাওয়া হয়নি। কথা ছিল ভাত খাবেন, ভাতও খাওয়া হয়নি। কাজ আছে বলে ভর দুপুরে বেরিয়ে গেলেন। এরপর বড়মামা এলে মা আগেই সতর্ক করে দেন যেন আমার সঙ্গে কোরান হাদিস বিষয়ে কোনও কথা না বলেন তিনি। একদিন বড়মামা এলেন শুক্রবারে। মাথায় একটি টুপি ছিল, সেটি খুলে, মার সামনে পকেটে পুরতে পুরতে বললেন, ‘আজকাল মসজিদে নামাজ পরার জন্য জায়গাই পাওয়া যায় না। এত ভিড়।’
মা নরম গলায় জিজ্ঞেস করেন, ‘তুমি কি মসজিদ থেইকা আইলা?’
বড়মামা বলেন, ‘হ। জুম্মাহ পইরা আইলাম।’ শুনে মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মুখে মধুর একটি হাসি।
আমি জোরে হেসে উঠি। বড়মামা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, ‘হাসস কেন? হাসির কি হইল? আমি তো পাঁচবেলা নামাজ পড়ি।’
এবার আরও জোরে হাসি।
মা বলেন, ‘নাসরিনডার যে কি হইব? ওর তো দোযখেও জাগা হইব না। মানুষ তো শুধরায়। মেবাইএর মত মানুষ যদি নিজের ভুল বুঝতে পাইরা তওবা কইরা নামাজ ধরতে পারে। তাইলে তুই কেন তওবা এখনও করস না?’
মা সেদিন বড়মামাকে বেশ আদর করে ভাত মাছ খাওয়ান। খাওয়ার পর ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বড় মামা উঁকি দেন আমার লেখার ঘরে। ঢুকে জোরে জোরে বলেন, ‘কি, সারাক্ষণ লেখা নিয়া থাকলেই চলবে! স্পেশালাইজেশনের জন্য তো গাইনিটাই ভাল। ডাক্তারি বিদ্যাটা এমন একটা বিদ্যা যেইটা দিয়া মানুষের সেবা অনেক বেশি করতে পারবি!’
‘ওই লেখাপড়া আমার আর হবে না।’ বলে আমি উদয় হওয়া একটি প্রশ্ন প্রায় করতে নিচ্ছিল!ম যে, ‘মোহাম্মদ মককা জয় করার পর যে আবদুল্লাহ নামের একটা লোকরে কতল করছিল, সেইটা কি সেই আবদুল্লাহ যে আবদুল্লাহ মোহাম্মদের আয়াত সংশোধন করত? আল্লাহর বাণী আবার সংশোধনের দরকার পড়ে কেন, এই প্রশ্নটা তার মনে জাগছিল বইলা যে পরে ইসলাম ত্যাগ করছিল?’ প্রশ্ন করার সুযোগ হয় না আমার। মা ঢোকেন। উদ্ভাসিত মুখ মার। বলেন, ‘মেবাই তুমি একটু নাসরিনরে বোঝাও ও যেন নামাজ শুরু করে।’
বড়মামা বলেন, ‘হ। নামাজ ত পড়া উচিত। এখন তো হাঁটাচলা বেশি হয় না ওর। নামাজ পড়লে শরীরের ব্যয়ামটা তো অন্তত নিয়মিত হয়।’
কথাটি মার পছন্দ হয় না।
মা আমাকে নামাজ পড়তে বলেন, কিন্তু কোরান যখন পড়ি, তিনি আঁতকে ওঠেন। টেবিলে ওপরে কোরান খোলা, এই একটু উঠে ও ঘরে গেলাম তো ফিরে এসে দেখি কোরান নেই, বিছানায় শুয়ে কোরান পড়ছি, পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেছি, ঘুম ভাঙলে দেখি বিছানায় কোরানটি নেই। শেষ পর্যন্ত কোরান উদ্ধার করি মার আলমারি থেকে। তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন।
‘কোরান শরীফ লুকাইয়া রাখো কেন?’
‘কোরান শরীফ পড়ছ কেন এত?’ সংশয়াপন্ন মার কপালে দুটো ভাঁজ।
‘বাহ, কোরান পড়া তো ভাল। সওয়াব হয়।’
‘তুই তো আর সওয়াবের জন্য পড়ছ না।’ মা বিরক্ত-কণ্ঠে বলেন।
হাসতে হাসতে বলি, ‘ছি ছি আর কইও না। আল্লাহ যদি জানেন যে তুমি কোরান পড়তে কাউরে বাধা দিতাছ তাইলে তোমারে হাবিয়া দোযখে নিক্ষেপ করবেন তিনি।’
মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ‘না হয় আমি হাবিয়া দোযখে যাই, তুই বেহেসতে যাওয়ার চেষ্টা কর।’
‘ওইটা চিন্তা কইর না। আল্লাহর সাথে কনটাক্ট হইছে আমার। বেহেসতের ব্যবস্থা পাককা। সেইদিন আল্লাহ আমারে জানাইলেন যে জান্নাতুল ফেরদাউসের লিস্টে চার নম্বরে আমার নাম।’
‘তাইলে তো ভাল। বেহেসতে যদি নাম থাকে।’
‘হ। তুমি তো দোযখের আগুনে পুড়তে থাকবা, আর আমি বেহেসতে। আল্লাহর কাছে তোমারে বেহেসতে আনার জন্য আমার তদবির করতে হবে।’
মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন, বলেন, ‘নাসরিন তর পায়ে পড়ি কোরানের বিরুদ্ধে আর কিছু লিখিস না। কোরান তো তরে কিছু করে নাই। মোল্লারা করতাছে মোল্লাদের বিরুদ্ধে লেখ।’
আমি সরে যাই মার কান্নার কাছ থেকে।
মাকে প্রায়ই দেখি জায়নামাজে বসে মোনাজাতের হাত তুলে চোখ বুজে বিড়বিড় করতে করতে ফুঁপোচ্ছেন। একদিন বিড়বিড়ের কাছে কান পেতে শুনি, বলছেন, ‘আল্লাহ তুমি আমার মেয়েরে কাফের বানাইও না। আল্লাহ তুমি আমারে মেয়েটারে কাফেরের সঙ্গ থেকে মুক্ত কর। আল্লাহ তুমি আমার মেয়ের বেহেসত নসীব কর। আল্লাহ তুমি আমার মেয়েরে সুমতি দাও, জ্ঞান দাও। আল্লাহ তুমি আমার মেয়ের হৃদয় মোহর করে দিও না।’
মার জন্য মায়া হয় আমার।
২২. ইস্তফা
সেই যে বিমানবন্দরে আমার পাসপোর্ট নিয়ে নিল পুলিশের লোকেরা আর আমাকে বলে দিল পরদিন যেন পাসপোর্ট ফেরত নিই মালিবাগের স্পেশাল ব্রাঞ্চের আপিস থেকে, পরদিন সেই আপিসে গিয়ে যখন আমার পাসপোর্ট চাইলাম, লোকেরা কিসের পাসপোর্ট কোন পাসপোর্ট, বলে দিল, কিছুই জানে না। পরদিন আবার গেলাম। তখনও পাসপোর্টের খবর নেই। পরদিন আবার।
‘আমার পাসপোর্ট নিয়ে যাবার কথা এখান থেকে। আমার পাসপোর্টটা দিন।’
‘পাসপোর্ট ওপরে আছে। ওখান থেকে পাঠালেই আপনি নিয়ে যেতে পারবেন।’
‘ওপরে মানে? কোন ওপরে?’ মাথার ওপরে কাঠের তাকে কয়েক টন কাগজের দিকে তাকাই।
‘আরে না, এই ওপরে না, এই ওপরে না।’
‘তাহলে কোন ওপরে?’
লোকটি পাজামা পাঞ্জাবি পরা, এক গাল হেসে বললেন, ‘স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে।’
‘ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বুঝি ওপর বলেন! তা ওপর থেকে কারা পাঠাবে পাসপোর্ট?’ ‘ওপরঅলারা।’
কয়েকদিন জুতোর সুকতলি খর্চা করে আমাকে এই শুনতে হল। পাসপোর্ট ওপরে আছে। ওপর থেকে আমার পাসপোর্টটি নিচে পাঠানোর অনুরোধ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সরাসরি একটি আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিই। আমার আবেদনে কোনও সাড়া কেউ দেয় না। পাসপোর্ট হাতে পেলেই বা কি লাভ! বহির্বাংলাদেশে ছুটিও তো পেতে হবে! ছুটি চেয়ে আবেদন করার পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রতিদিন যাচ্ছি। মহাপরিচালক হয় ব্যস্ত, নয় এখনও আপিসে আসেননি। এরপরও ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে যেদিন তাঁর দেখা মিলল, মুখোমুখি হই।
‘কি ব্যপার, কি চাই?’ মহাপরিচালক চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখেন।
‘সই চাই।’
‘কিসের সই?’
‘অনেকদিন হল আমি একটা দরখাস্ত দিয়ে রেখেছি এক্সবাংলাদেশ লীভের জন্য। সই করে দেন।’
‘সই করা যাবে না।’
বুকে আমার একটি পাথর ছোঁড়ে কেউ। একটি যন্ত্রণা বুক বেয়ে কন্ঠদেশ বেয়ে চোখে উঠে আসে। তাহলে কলকাতার অনুষ্ঠানে যাওয়া আমার হচ্ছে না!
‘কেন যাবে না সই করা?’ প্রশ্নটি করি।
‘ওপর থেকে অনুমতি এলে সই করব।’
‘কোন ওপর থেকে?’
‘স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে।’
‘অন্য কোনও ডাক্তারের বেলায় কি সই দিতে ওপরের অনুমতি লাগে?’
মহাপরিচালক তাঁর কালো চশমাটি খুলে ফেললেন। আমি খুব বেয়াদবের মত এই প্রশ্নটি করেছি বলে তাঁর ধারনা। কঠিন কণ্ঠে বললেন, ‘না কারও জন্য ওপরের অনুমতির দরকার হয় না। কিন্তু আপনার জন্য দরকার হয়।’
কেন হয়? এই প্রশ্নও আমি করি।
তিনি এবার তাঁর টেবিলের একটি কাগজের দিকে ঝুঁকে বললেন, ‘নিজেই আপনি জানেন।’
‘না, আমি তো জানি না। আমার জন্য আলাদা নিয়ম কেন, তা আমার জানার ইচ্ছে।’ মহাপরিচালকের মুখের দিকে আমি তাকিয়ে থাকি উত্তরের আশায়।
তিনি তাঁর চিবুক উঁচু করে ধরেন।
‘তাহলে এক কাজ করেন। নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকেন। উত্তর একসময় পাবেন।’
‘উত্তর আমাকে নিজে পেতে হবে কেন, যেহেতু এটা আপনাদের তৈরি করা নিয়ম, সেহেতু আপনাকেই জানাতে হবে উত্তর।’
যেন তিনি আমার কথা শোনেননি, এমনভাবে, বসে থাকা অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কথা বলতে শুরু করলেন, ‘কি খবর আপনার! ওদিকে এখন কেমন অবস্থা? গরম পড়েছে আজকাল খুব। হে হে হে হে।’
মহাপরিচালকের হেহেহে তখনও শেষ হয়নি, আমি প্রশ্ন করি, ‘হেলথ মিনিস্টি থেকে পারমিশান দেওয়া হচ্ছে না কেন? এর কারণ কি?’
এবার মুখ ফেরান আমার দিকে, চোয়ালভাঙা মহাপরিচালকের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে টেবিলের ওপর তাঁর হাতের তলে যে ফাইলটি, সেটি খুলে আমার দরখাস্তের একটি কপি তুলে নিয়ে বললেন, ‘সই করে মিনিস্ট্রিতে আপনার দরখাস্ত পাঠালেই কি না পাঠালেই কি! আপনার ছুটি শুধু হেলথ মিনিস্ট্রির ব্যপার না। মেইনলি এটা হোম মিনিস্ট্রির ব্যপার। হোম মিনিস্ট্রি থেকে পারমিশান না পেলে আপনার ছুটি হবে না।’ টেবিলে আর কোনও ফাইল নেই, কেবল আমার ফাইলই। আশ্চর্য, আমার এই ফাইল কেন এত জরুরি এই অধিদপ্তরে! আমি ঘরে ঢোকার পর এই ফাইলটি তিনি খুঁজে বের করে টেবিলে রাখেননি। এটি রাখাই ছিল টেবিলে। অধিদপ্তরে সব ডাক্তারের একটি করে ফাইল থাকে। ফাইল খুললেই ডাক্তারের চাকরি এবং বদলি সংক্রান্ত কাগজ বেরোয়। যখন হৃষ্টপুষ্ট ফাইলটি খুলে আমার দরখাস্তটি দেখালেন, ফাইলের ভেতর পত্রিকার অনেকগুলো কাগজ চোখে পড়ল। পত্রিকার কাগজ আমার ফাইলে কেন!
এরপর আরও আরও দিন যেতে থাকি মহাখালির স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে। হাসপাতালের ডিউটি শেষ করে সোজা মহাখালি। প্রতিদিন বাড়ি ফিরি শেষ বিকেলে। মা আমার শুকনো মুখ দেখে জিজ্ঞেস করেন, ‘এত দেরি কইরা ফিরস কেন আজকাল। সেই যে সকালে দুইডা বিস্কুট খাইয়া গেছস। সারাদিন ত পেটে কিছু পড়ে নাই।’ মা রান্নাঘরে দৌড়ে যান, আমার জন্য ভাত তরকারি বেড়ে নিয়ে আসেন। ক্ষুধার্ত পেট কোনওরকম শান্ত করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায়। পরদিন গিয়ে আমাকে আবারও শুনতে হয় ওপরের অনুমতি জোটেনি। ওপরের অনুমতি জোটাতে হলে ওপরে যেতে হয়। ওপরে গিয়েও দেখি আমাকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না ভেতরে ঢোকার। না স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে। না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে।
এদিকে ইনকিলাবে আমার পাসপোর্টের ছবি ছেপে লিখেছে আমি ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশ যেতে চেয়েছিলাম। সরকার যেন আমার জন্য একটি কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করে। আমার পাসপোর্ট আমার নাগালে নেই, তা ইনকিলাবের নাগালে কি করে যায়! তাহলে কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ইনকিলাবের বেশ দহরম মহরম। স্বরাস্ত্রমন্ত্রী আবদুল মতিল চৌধুরী নিজে একজন রাজাকার ছিলেন একাত্তরে। পাকিস্তানি বাহিনীর হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় কাঁচপুর সেতু পাহারা দিতেন তিনি। আজ তিনি মন্ত্রী হয়েছেন এ দেশের, যে দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি একদা লড়েছিলেন। সেই যে জিয়াউর রহমান শুরু করেছিলেন রাজাকারদের ক্ষমতায় বসাতে, সেই থেকে চলছে রাজাকারের রাজত্ব। এখন মুক্তিযোদ্ধারা পড়ে থাকেন পঙ্গু হাসপাতালে, রাজাকাররা মন্ত্রণালয়ে। আশঙ্কারা পিলপিল করে আমার শরীর বেয়ে ওঠে, লোমকূপে বাসা বাঁধে। ইনকিলাবের লোকেরা ভাল জানে যে এটি কোনও ভুয়া পাসপোর্ট নয়। পেশা আমি ডাক্তারি না লিখে কেন সাংবাদিকতা লিখেছি, সেটি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। পাসপোর্টে আমার নাম, আমার বাবার নাম, আমার উচ্চত!, আমার ঠিকানা, বয়স, এমন কী আমার বাঁ চোখের ওপর আমার কালো তিলটির কথা লেখা। কিছুই অসত্য নয়। আমার পেশাতেও কিন্তু অসত্য কিছু নেই। সাংবাদিকতাও আমার পেশা। এটি আমার পছন্দের পেশা বলে পাসপোর্টে পেশার ঘরে ডাক্তারি না বসিয়ে সাংবাদিকতা বসিয়েছি। ইনকিলাবের লোকেরা, আমি যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তার কারণ হিসেবে কেবল আমার পাসপোর্টটি ভুয়া এই বলেই শেষ করেনি, আমার লেখার উদ্ধৃতিই দিয়েছে বেশি। ধর্ম নিয়ে, দুই বঙ্গ নিয়ে, সরকারের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে এ যাবৎ যা লিখেছি, সেসব থেকে উদ্ধৃতি। যেহেতু আমি এসব লিখি, তাই সরকার যেন অচিরে আমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে দেশ ও জাতির সেবা করেন। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিটি কি হতে পারে, তাও ইনকিলাবের লোকেরা বলে দিয়েছেন, ফাঁসি। মাওলানা মান্নানের পত্রিকা ইনকিলাব, সেই মাওলানা মান্নান, একাত্তরে যিনি ছিলেন পাকিস্তানী বাহিনীর জানি দোস্ত। আজ তিনি প্রচার মাধ্যমের মোগল। আশঙ্কারা আমাকে টুকুস টুকুস করে কামড় দেয়। আশঙ্কারা আমার ত্বক কেটে ঢুকে পড়ে শরীরের ভেতর, আমার হৃদপিণ্ডে, ফুসফুসে, আমার রক্তে, আমার মস্তিস্কের কোষে কোষে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে তারপরও আমি যাই। না, ওপর থেকে আমার বহির্বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করার জন্য কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। মহাপরিচালক সোজাসুজি বলে দিলেন, আপনার ছুটি মঞ্জুর হবে না। কেন হবে না? ইনকিলাবে লেখালেখি হচ্ছে, তাই হবে না। আশ্চর্য ইনকিলাব কি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মা বাপ! আমার ব্যপারে সিদ্ধান্ত নেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। ডাক্তার হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনও নিয়ম আমি মেনেছি কি মানিনি, যদি না মানি, তার শাস্তি কি হবে, তা দেখার দায়িত্ব স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের, ইনকিলাবের নয়। অবশ্য বহির্বাংলাদেশ ছুটির আর প্রয়োজন নেই ততদিনে। কলকাতার অনুষ্ঠান শেষ, দেশের কবিরা দেশে ফিরে এসেছেন।
অগত্যা পাসপোর্টটি ফেরত পেতে, অর্থাৎ আমার নাগরিক অধিকারটি ফেরত পেতে মালিবাগের স্পেশাল ব্রাঞ্চের আপিসে আবারও যাই। গিয়ে দেখি আবদুস সাত্তার লোকটি, যে লোকটি ওপর থেকে আমার পাসপোর্ট আসার কথা আমাকে বলেছিলেন, বই পড়ছেন খুব মন দিয়ে। বইয়ের বাক্যে বাক্যে লাল কালির দাগ। হাতে তাঁর একটি লাল কলম। টেবিলের এক কোনায় যত বই আমি লিখেছি এ যাবৎ, সবগুলো বই। আমাকে দেখে লোকটি বই গুটিয়ে রাখার প্রয়োজন মনে করলেন না। আমি একটি চেয়ার টেনে সামনে বসে জানতে চাইলাম ‘পাসপোর্টের খবর কি, ওপর থেকে এসেছে?’
তিনি ওপরের প্রসঙ্গে না গিয়ে বললেন, তদন্ত চলছে।
‘কিসের তদন্ত?’
‘আপনার বই পড়ার হুকুম এসেছে। কোথায় আপত্তিকর কি কি লিখেছেন, সেসব দেখতে হচ্ছে।’
‘পাসপোর্টের সঙ্গে আমার বইয়ের সম্পর্ক কি?’
তদন্তকারী অফিসারের ঠোঁটের কিনারে একটি হাসি ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল। তিনি এর কোনও উত্তর দিলেন না। খানিকপর বললেন, ‘ধর্ম নিয়ে আপনি খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন!’
‘মানে?’
‘খুব বাজে কথা লিখেছেন। এইসব লেখেন কেন?’
‘আমি যা বিশ্বাস করি, তা লিখি। কিন্তু আমার লেখার সঙ্গে তো পাসপোর্ট না দেওয়ার সম্পর্ক থাকতে পারে না। পারে কি?’
আবদুস সাত্তার আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে গিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়েছি। মহাপরিচালক আমাকে দেখে মধুর হাসি উপহার দিয়ে বললেন, ‘এইতো বিখ্যাত লেখিকা এসে গেছে। বসেন বসেন।’
আমি মহাপরিচালকের রসিকতার ঝাঁজ সামলে নিয়ে চেয়ারে বসি।
‘আপনার কলাম তো পড়ি পত্রিকায়।’ মহাপরিচালক হাসলেন বলতে বলতে।
ও। ও শব্দটি উচ্চারণ করে আমি চুপ হয়ে থাকি।
‘আপনি যে পত্রিকায় লেখেন, কিভাবে লেখেন?’
‘কিভাবে লিখি মানে! আগে হাতে লিখতাম। এখন কমপিউটারে লিখি।’
‘বেশ ভাল কথা, এখন কমপিউটারে লেখেন। আপনি তো শুধু পত্রিকায় লেখেন না, বইও তো লেখেন।’
‘হ্যাঁ লিখি।’
‘সরকারের কাছ থেকে পারমিশান নিয়েছেন?’
‘তার মানে?’
‘এই যে লেখেন, পত্রিকায় কলাম লেখেন। সরকারের পারমিশান ছাড়া লেখেন?’
আমার কপালে ভাঁজ পড়তে থাকে। এ সব কী শুনছি!
‘সরকারের পারমিশান লাগবে নাকি লিখতে হলে?’
‘নিশ্চয়ই। সরকারি চাকরি করেন, সরকারি পারমিশান ছাড়া কী করে লিখবেন! হ্যাঁ লিখতে পারেন, ঘরে বসে লিখতে পারেন। কিন্তু কোথাও ছাপার অক্ষরে বেরোনোর আগে সরকারের পারমিশান লাগবে।’
‘এরকম নিয়ম নাকি?’
‘হ্যাঁ এরকম নিয়ম।’
‘কিন্তু এত যে লেখক আছেন, পত্রিকায় লিখছেন, বই লিখছেন, তাঁরা তো অনুমতি নিচ্ছেন না সরকারের!’
‘আপনি জানেন কি করে যে নিচ্ছেন না!’
‘আমি জানি।’
‘নিচ্ছেন নিচ্ছেন।’
একটি যন্ত্রণা আমার ঠোঁটে উঠে এলে বলি, ‘কি করে অনুমতি নিতে হয়, বলবেন!’
‘যা ছাপতে চান, আগে তা সরকারের কাছে জমা দেবেন, তারপর যখন সরকার বলবে যে হ্যাঁ এই লেখা ছাপার জন্য পারমিশান দেওয়া গেল, তখন ছাপতে দেবেন। ভেরি সিম্পল।’
‘এই নিয়মটা কি কেবল আমার জন্যই নাকি?’
মহাপরিচালক অপ্রতিভ একটি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, ‘আপনার জন্য হবে কেন! এই নিয়ম সবার জন্য!’
‘যদি আমি পারমিশান না নিয়ে ছাপি লেখা, তাহলে কি হবে?’
‘তাহলে আপনি আইন অমান্য করলেন। আইন অমান্য করলে কি হয়, তা তো নিশ্চয়ই জানেন!’
আমি স্পষ্ট বুঝি যে মহাপরিচালক এসব কথা আমাকে বলছেন ওপরের আদেশ পেয়ে। ওপরের সিদ্ধান্তই তিনি আমাকে জানাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আর কোনও কথা বলতে আমার ইচ্ছে হয় না। মাথা বনবন করে ঘুরতে থাকে। আমি বেরিয়ে যাই। মহাখালির মোড় থেকে একটি রিক্সা নিয়ে সোজা বাড়িতে। বাড়িতে কারও সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। মা খাবার নিয়ে আসেন। খাবো না বলে দিয়ে শুয়ে থাকি। জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে থাকি। জানালার ওপারে আকাশ, আকাশে মেঘ উড়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে! কী চমৎকার ওরা উড়ে যায় ঠিকানাবিহীন। নাকি মনে মনে ওদেরও কোনও ঠিকানা থাকে। হঠাৎ আমি শোয়া থেকে উঠে পড়ি। বুকের ভেতরকার ধ্বক ধ্বক শব্দ আমি চাইলেও থামাতে পারছি না। অস্থির পায়ে এঘর ওঘর করতে থাকি। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, এদিক ওদিক তাকাই, তাকাই কিন্তু কিছুই আমার চোখে পড়ে না। সব কিছুই শূন্য শূন্য লাগে, যেন এক আকাশ ছাড়া আর কিছু নেই কোথাও। বিশাল আকাশটির তলে আমি একলা পড়ে আছি। ইচ্ছে হচ্ছে চিৎকার করে কাঁদি, কিন্তু কাঁদতে পারছি না। এসব মার নজরে পড়ে, আর কারওর না পড়লেও।
‘নাসরিন, কি হইছে?’ মা জিজ্ঞেস করেন।
‘কিছু না।’
‘কিছু একটা নিশ্চয়ই হইছে। আমারে বল কি হইছে।’
আমি জোরে ধমক দিই, ‘প্যাঁচাল পাড়বা না তো। কিছু হয় নাই।’
মা চুপ হয়ে যান।
এক গেলাস লেবুর শরবত বানিয়ে আমার হাতে দেন। শরবত ঢক ঢক করে খেয়ে আবার আমি বিছানায় কুকুর কুণ্ডুলি হই। মা পাশে বসে একটি হাত রাখেন আমার মাথায়। চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে নরম গলায় বলেন, ‘এত অস্থির অস্থির করতাছ কেন? ঘুম ধরলে কিছুক্ষণ ঘুমাও।’
দীর্ঘশ্বাস বেরোয় আমার কণ্ঠ থেকে। নিজের একটি ম্লান কণ্ঠস্বর নিজেই শুনি, ‘মা, আমার লেখালেখি ছাইড়া দিতে হইব।’
‘কেন ছাড়তে হইব?’
‘আমার ওপর আদেশ জারি হইছে। তারা আমার জন্য নিয়ম খুইঁজা বাইর করছে। আইন দেখায়। সরকারি চাকরি করলে লেখালেখি করা যাবে না।’
‘তরে কত কইছি ধর্ম নিয়া লেখিস না। নারী নির্যাতন নিয়া লেখতাছিলি, তা তো ভালই ছিল। কেন খালি খালি ধর্মের সমালোচনা করতে গেলি! কথা কইলে তো শুনস না। এখন কি করবি? তাদেরে জানাইয়া দে, ধর্ম নিয়া আর লিখবি না, সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লিখবি না বইলা দে।’
আমার ঘুম পায়। মার কথাগুলো ধীরে ধীরে খুব দূরের মনে হতে থাকে।
আমার সামনে এখন দুটি পথ। এক হল লেখা, আরেক হল সরকারি চাকরি। যে কোনও একটি আমার বেছে নিতে হবে। আমি লেখাকে বেছে নিই। কাউকে কিছু না বলে, কারও সঙ্গে কিছু না বুঝে, দেশের দ্য বেস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাকরি রত অবস্থায় আমি একটি কাণ্ড করি, একটি সাদা কাগজ নিয়ে তাতে লিখি, মাননীয় মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জনাব, বিনীত নিবেদন এই যে আমি, তসলিমা নাসরিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অ্যানেসথেসিয়া বিভাগে কর্মরত মেডিকেল অফিসার য়েচ্ছ!য় সজ্ঞানে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছি। আমার এই ইস্তফা পত্র গ্রহণ করে আমাকে বাধিত করবেন। আশা করি অতি সত্ত্বর আমার এই ইস্তফাপত্র গ্রহণ করে আমাকে সরকারি নাগপাশ চাকরি থেকে মুক্ত করা হবে।
লিখে, সই করে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিজে গিয়ে আমার ইস্তফাপত্র দিয়ে আসি। ইস্তফাপত্র কেবল দিলেই তো চলবে না, এটি গ্রহণ করা হল কি না, তারও খোঁজ নিতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দিনের পর দিন গিয়েও ইস্তফা পত্রটি সরকারিভাবে গ্রহণের কোনও কাগজ আমার পাওয়া হয় না। কাগজটি পেলে আমি যে সরকারি চাকরিতে আর নেই, সে প্রমাণ দেখিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে আমার পাসপোর্ট ফেরত চাওয়ার দাবি করতে পারব। আমার এই ইস্তফার খবর পেয়ে বাবার মাথায় হাত, এ কি কাণ্ড করেছে মেয়ে, এর মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি! বাড়ির সকলের ধারণা আমার সত্যিই মাথার ঠিক নেই। যেই শোনে, থ মেরে যায়। বন্ধুরাও। অবিশ্বাস্য একটি কাণ্ড বটে। সরকারি চাকরি লোকে হাজার তপস্যা করেও পায় না, সরকারি চাকরি পাওয়া যেমন কঠিন এবং যাওয়াও তেমন কঠিন। লোকে কয়েক লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েও পাঁচশ টাকার সরকারি চাকরি যোগাড় করতে চায়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অনুপস্থিত থাকলেও, কাজে অবহেলা করলেও আর যাই যাক, সরকারি চাকরি যায় না, সরকারি চাকরি একটি মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা, আর আমি কি না জীবনের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা, তাও আবার ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসার পদের এত ভাল একটি চাকরিটি শখ করে ছেড়ে দিয়েছি! হ্যাঁ দিয়েছি ছেড়ে, দ্বিতীয়বার আমি ভেবে দেখি না।
এর মধ্যেই হঠাৎ দেখি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমার পদটিকে শূন্য পদ উল্লেখ করে সেই পদে অন্য এক ডাক্তারকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। বেশ ভাল কথা, এর মানে আমার ইস্তফা পত্র তোমরা গ্রহণ করেছো। আমাকে সাদরে ইস্তফা দিয়েছো, তাই আমার পদটিকে শূন্য পদ বলছো, এর মানে আমি ওই পদটিতে নেই, আমি তবে কোথায়, আমাকে তো কোথাও বদলিও করোনি, কোনও ডাক্তার মরে গেলেই পদটি শূন্য হয়। আমি তোমাদের কাছে মৃত একজন মানুষ। ইস্তফা দিলে তো মৃতই হয়, কিন্তু আমাকে কেন বলছো না যে ‘তোমাকে ইস্তফা দেওয়া হইল, তুমি এখন আমাদের সকল বদমায়েশি, সকল ষড়যন্ত্র, নোংরামি, সকল কুটিলতা জটিলতা হইতে মুক্ত!’ না সেরকম কোনও চিঠি আমার কাছে আসে না। কয়েক মাসের বকেয়া মাইনেও আমাকে দেওয়া হয় না। সরকারি রেভিন্যূ আপিসে অনেকদিন ধর্না দিয়েও আমি আমার পাওনা টাকা আদায় করতে পারি না। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দেওয়া আমার ইস্তফাপত্রের একটি অনুলিপি আর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমার জায়গায় অন্য ডাক্তারকে চাকরি দেওয়ার কাগজটি পাঠিয়ে দিই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে, সঙ্গে আমার পাসপোর্ট ফেরত চেয়ে আবেদন। আমি তো এখন সরকারি চাকরি করছি না, আমি সম্পূর্ণ বেসরকারি মানুষ। পাসপোর্টে আমার যে পেশাটি দেওয়া আছে, পুরোদস্তুর সে পেশায় আমি নিয়োজিত। সুতরাং অনুগ্রহপূর্বক আটককৃত ছাড়পত্রটি এই অধমকে ফিরত দিয়া বাধিত করিবেন। তারপরও কোনও সাড়াশব্দ নেই। আমার পাসপোর্টও ফেরত দেওয়া হয় না। পাসপোর্ট আমি ফেরত চাই, দেশের বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্য নয়, এটি আমার নাগরিক অধিকার বলে চাই। অধিকার কেড়ে নিয়ে অন্যায়ভাবে আমার পাসপোর্ট আটক করা হয়েছে এবং ততোধিক অন্যায়ভাবে আমি সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার পরও আমার পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হচ্ছে না, সে কারণেই চাই। কিন্তু আমার কথা কে শোনে! সাড়াশব্দ না পেয়ে পাসপোর্ট আপিসে গিয়ে নতুন একটি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করি। নাহ, নতুন কোনও পাসপোর্টও আমাকে দেওয়া হয় না।
একদিন, তখনও সরকার লজ্জা নিষিদ্ধ করেনি, নাহিদ, আইনের মেয়েটি, আমাকে বলল যে তার এক চেনা লোক আছে, লোকটি জামাতপন্থী, আবার সরকারের লোকদের সঙ্গেও বেশ ওঠাবসা আছে, লোকটি তাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে রাত আটটার দিকে নিয়ে যেতে পারবে। নাহিদই চেনা লোকটিকে অনুরোধ করেছে এই ব্যবস্থাটি করার জন্য। সুতরাং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমার পাসপোর্ট নিয়ে নাহিদ একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়েছে কথা বলার। ভাল কথা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠানো আমার আবেদপত্রটির একটি অনুলিপি নাহিদ নিয়ে গেল তাঁর বাড়িতে। ঘন্টা দুই পর মেয়ে তার বিষণ্ন মুখটি নিয়ে ফেরত আসে।
কি হল?
‘বস, আপনের আবেদনপত্র উনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।’
‘তাই নাকি!’
‘হ্যাঁ, বললেন, এই মেয়ে ধর্মের বিরুদ্ধে লেখে। আমাদের রাসুলল্লার বিরুদ্ধে জঘন্য সব কথা লেখে। একে তো পাসপোর্ট দেবই না। এর লজ্জা ব্যান করব।’
‘এই কথা বললেন?’
‘হ্যাঁ এই কথা বলে খুব জোরে জোরে হাসলেন।’
‘তুমি কিছু বললে না?’
‘বললাম, লজ্জা ব্যান করবেন কেন? ওতে কি কোনও আপত্তিকর কথা আছে? বললেন, আছে আছে নিশ্চয়ই আছে। বললাম, কিছু তথ্য দেওয়া, তথ্য তো উনি বানিয়ে লেখেননি। বললেন, তা হয়ত বানাননি। কিন্তু এভাবে কোন হিন্দুকে চড় দেওয়া হল, কোথায় গাল দেওয়া হল, কার বাড়ির বেড়ায় আগুন লাগল, এসব সব জানানো উচিত? মালাউনের বাচ্চারা তো লাই পেয়ে মাথায় উঠবে।’
নাহিদ একটি সিগারেট ধরায়। আরেকটি বাড়ায় আমার দিকে।
‘নাহ, সিগারেট খাবো না।’
‘আরে বস, খান খান। আপনি খুব টেনশানে আছেন। খেলে টেনশান কমবে।’
আমার বাড়ির কেউই নাহিদকে পছন্দ করে না। কারণ নাহিদ সিগারেট খায়। সিগারেট জিনিসটি আমারও পছন্দ নয়। কিন্তু নাহিদ আমার ঘরে বসে সিগারেট ধরাবেই এবং আমাকে এক টান দু টান তিন টান দেওয়ার জন্য সাধাসাধি করবে। বস বলে ডাকা আমি পছন্দ না করলেও সে আমাকে বস বলে ডাকবে। নাহিদ খুব সাহসী মেয়ে। সাহসী মেয়েদের আমার খুব ভাল লাগে। রাত বিরেতে সে তার নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে বাসে করে রওনা হয়। আমি জিজ্ঞেস করি, তুমি কি ভয় পাও না নাহিদ?
‘বস, আপনার মুখে ভয়ের কথা মানায় না। ভয় পাবো কেন? কেউ কিছু করলেঞ্চ, নাহিদ তার হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে, ‘ঘুসি দিয়ে ফেলে দেব না!’
নাহিদের ডান হাতের ছ নম্বর আঙুলটি মুঠির বাইরে অসহায় পড়ে থাকে।
নাহিদ কখনও শাড়ি পরে না। জামা পাজামা ওড়না। পায়ে সেণ্ডেল। এই হল তার চিরাচরিত পোশাক। মুখে কখনও কোনও রং মাখে না সে। ফাঁক পেলেই আমার বাড়িতে চলে আসবে, বলবে, ‘বস, কিছু কাজ আছে? থাকলে বলেন, করে দিই।’ কাজ থাকলে করবে, না থাকলে গলা ছেড়ে গান গাইবে।
ঠিক ঠিকই লজ্জা নিষিদ্ধ হল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খ্যাক খ্যাক করে হেসে বললেন, ‘ওর বাকি বইও ব্যাণ্ড করব।’ দেশের স্বাধীনতার শত্রুটি আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আজ তাঁর ভারি নিতম্বের তলে লেখকের লেখার স্বাধীনতা, তার মত প্রকাশের অধিকার থেতলে যাচ্ছে।
ভেবেছিলাম সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিলেই সরকারের রোষ মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে লেখালেখি করতে পারব। কিন্তু এই স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হবে কেন! আমি আপাদমস্তক বেসরকারি হলেও আমার গতিবিধির ওপর সরকারের কড়া নজর। একদিন স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুটো লোক আমার শান্তিনগরের বাড়িতে উপস্থিত। প্রথম দরজা খুলিনি। এরপর এমন জোরে ধাককা দিতে শুরু করল দরজা, চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘পুলিশের লোক, দরজা খোলেন।’ ভয়ে ভয়ে দরজা খোলা হল। লোকদুটো সদর্পে ঘরে ঢুকলেন, যেন নিজেদের কোনও হরিহর আত্মার বাড়িতে ঢুকেছেন। দিব্যি হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন ঘর জুড়ে, বৈঠকঘরের পাখা চালিয়ে দিয়ে, জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে সোফায় বসে গেলেন হাত পা ছড়িয়ে। একজনের মুখে মিটিমিটি হাসি, আরকজনের চোখের ভুরু যথাসম্ভব কোঁচকানো।
ভুরু প্রথম মুখ খুললেন, ‘লজ্জা বইটা আছে আপনার কাছে?’
বুকের মধ্যে একটি ঠাণ্ডা জলের গেলাস উপুড় হয়ে পড়ে। আমার কাছে লজ্জা বইটি আছে। কিন্তু এটির সংরক্ষণ যেহেতু নিষিদ্ধ, এটি আমার কাছে সংরক্ষিত দেখলে লোকদুটো আমাকে এই মুহূর্তে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমি হ্যাঁ বলব নাকি না বলব ঠিক বুঝে পাই না।
‘কেন? আপনার দরকার?’ উল্টো প্রশ্ন করি।
ভুরু বলেন, ‘হ্যাঁ একটা বই আমার দরকার।’
‘বইটার তো সংরক্ষণ নিষিদ্ধ!’ আমি বলি। আমি ভুরুর মুখোমুখি। মিটিমিটি আমার ডান পাশে।
‘আছে বই?
‘না।
‘ঠিক তো!’
‘ঠিক।’
নির্লিপ্ত স্বর। দুজনের দুজোড়া পায়ের দিকে চোখ আমার। এঁরা যদি এখন আমার লেখার ঘরটিতে যান, নিশ্চয়ই একটি লজ্জা কোথাও পাবেন। তখন কী হবে না ভেবেই আমি ঠিক শব্দটি বলেছি। কথোপকথন শুনে মা যদি কোথাও বইটি পেয়ে লুকিয়ে রাখেন তবেই বাঁচোয়া। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠি, ভুরু আমাকে থামিয়ে বলেন, ‘কোথায় যাচ্ছেন, বসেন বসেন।’ উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়া আমাকে বসতে হয়। এক গাদা অস্বস্তি আর অরুচি নিয়ে বসি। বুকের মধ্যে একটি ভয়ও কোত্থেকে যেন উড়ে এসে বসে।
এবার মধ্যবয়স্ক মিটিমিটি বলেন, ‘আপনার লজ্জা কেন বাজারে বিক্রি হচ্ছে?
‘আমার প্রকাশক বিক্রি করছে না লজ্জা। তার কাছে নেইও তো লজ্জা। সব তো পুলিশ নিয়ে গেছে।’
‘কিন্তু বিক্রি তো হচ্ছে! কেন হচ্ছে?’
‘তা আমি জানি না কেন হচ্ছে, কী করে হচ্ছে।’ গম্ভীর গলায় বলি।
‘আপনার তো জানার কথা।’
আমার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। বলি, ‘আমি বইটা লিখেছি। বইয়ের লেখক আমি। এই বই বিক্রি করার দায়িত্ব আমার না। যারা বিক্রি করছে তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করেন কেন তারা বিক্রি করছে।’
যে চিকন একটি ভয় ছিল, সেটি উবে যায়। কেবল অস্বস্তি আর অরুচিগুলো পড়ে থাকে। ভুরু মুখ খোলেন, ‘ফেরা.. .
শব্দটি খপ করে ধরে মিটিমিটি বলেন, ‘ফেরা বইটা কেন লিখেছেন?’
‘কেন লিখেছি মানে? ইচ্ছে হয়েছে লিখতে তাই লিখেছি।’
ফেরা নামের একটি গল্প লিখেছি নতুন। পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যার জন্য দুলেন্দ্র ভৌমিক একটি উপন্যাস চেয়েছিলেন। কিন্তু উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়নি, লিখেছি বড় গল্প, যদিও পত্রিকায় উপন্যাস হিসেবেই ফেরা ছাপা হয়েছে। ফেরা বই হয়ে বেরিয়ে গেছে দেশে, তবে পশ্চিমবঙ্গে বই হয়নি এখনও। আমার লেখার সঙ্গে সঙ্গেই বই ছাপা হয়ে যেতে পারে, কারণ আমি কমপিউটারে যে বাংলা লিপিতে লিখি সেই একই লিপি ব্যবহার করেন বাংলাদেশের প্রকাশকরা। আমি লিখে ডিসকেটে কপি করে দিলেই তাঁরা সোজা ছাপতে চলে যেতে পারেন প্রেসে। কম্পোজ করা, প্রুফ দেখা এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত। কিন্তু আনন্দ পাবলিশার্সএর সব কিছুই শুরু থেকে করতে হয়, যেহেতু ওখানে বাংলা আদর্শলিপি ব্যবহার হয় না। ফেরার গল্পটি খুব ছোট, পূর্ববঙ্গের এক কিশোরী মেয়ে যাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে তার নিরাপত্তার জন্য, একদিন সে ফিরে আসে নিজের দেশটি দেখতে, তিরিশ বছর পর। সেই দেখাটি কেমন, তারই বর্ণনা। এখন পুলিশের লোক জানতে চাইছেন আমি কেন লিখেছি ফেরা। আমার ইচ্ছে হয়েছে বলে লিখেছি এই উত্তরটি তাঁদের মনঃপূত হচ্ছে না, বুঝতে পারি।
‘ফেরা আপনাকে কে লিখতে বলেছে?’ ভুরু।
‘মানে?’
‘কেউ তো নিশ্চয়ই বলেছে যে ফেরা নামে এরকম একটা গল্প নিয়ে একটা উপন্যাস লেখেন। কে বলেছে?’
‘প্রকাশকরা তো সবসময়ই বলছেন লিখতে। কিন্তু কি নাম হবে উপন্যাসের, কী গল্প আমি লিখব, তা আমাকে কেউ বলে দেন না। সে আমি নিজেই লিখি।’
‘ফেরার গল্পটা তো আর আপনার মাথা থেকে আসেনি। নিশ্চয়ই কেউ আপনাকে বলে দিয়েছে।’
‘না। কেউ বলে নাই। আমি তো বললামই, কি গল্প আমি লিখব সেটা আমিই ঠিক করি।’
‘ফেরার কোনও ক্যারেকটার কি আপনার চেনা? মানে আপনি কি চেনেন কল্যাণী নামের কোনও মহিলাকে?’
‘না।’
‘তাহলে কেন লিখেছেন যে কল্যাণী নামের একজন হিন্দু মহিলা কলকাতা থেকে এখানে এসেছে বাড়িঘর দেখতে!’
‘আশ্চর্য, এটা তো গল্প!’
‘বানিয়ে লিখেছেন তাহলে! এরকম কোনও ঘটনা ঘটে নাই।’
‘গল্প তো লেখকরা তাদের কল্পনা দিয়েই লেখেন।’
‘কিন্তু বাস্তবের সাথে তো কিছু মিল থাকতে হয়। তাই না? নাকি উদ্ভট উদ্ভট কল্পনা লিখে দিলেই হয়ে যায়!’
‘কলকাতায় বইটা বের হয়েছে?’ মিটিমিটি।
‘বই হয়ে বেরোয় নি।’
‘কি হয়ে বেরিয়েছে?’
‘পত্রিকায় গল্পটা ছাপা হয়েছে।’
‘কোন পত্রিকা?’
‘আনন্দলোক।’
‘হুম।’
‘আছে আপনার কাছে পত্রিকাটা?’
আমার গা জ্বলে। ইচ্ছে করে ঘাড় ধরে যদি লোকদুটোকে বের করে দিই। বাইরের লু হাওয়া এসে আমার জ্বলুনি আরও বাড়াচ্ছে।
‘পত্রিকাটা আছে?’ ভুরু।
‘না।’ একটু জোরেই এই না টা বলি।
‘আপনি মুসলমান হয়ে হিন্দুদের নিয়ে গল্প লেখেন কেন?’
‘আমি মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়েছি। কিন্তু আমি কোনও ধর্ম বিশ্বাস করি না।’ বলি, জোর দিয়ে। এটি বলে যে একগাদা অস্বস্তি আর অরুচি ছিল, সেটিও দেখি সরে যাচ্ছে আমার ভেতর থেকে। যেন অনেকক্ষণ সিন্দুকে বসে থাকার পর খোলা হাওয়ায় এসে বুক ভরে শ্বাস নিলাম।
‘ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস নাই আপনার?’ ভুরু জিজ্ঞেস করেন।
‘না।’
‘অন্য কোনও ধর্মে আছে বিশ্বাস?’
‘না।’
‘হিন্দু ধর্মে আছে?’
‘না।’
‘তাহলে হিন্দুর পক্ষে এত কথা বলেন কেন?’ মিটিমিটির প্রশ্ন।
‘কথা বলি, কারণ ওরা মানুষ। আমি কোনও ধর্ম দেখি না। আমি দেখি মানুষ। কোনও মানুষের ওপর যদি অযথা অত্যাচার করা হয়, আমি সেই মানুষের পক্ষে দাঁড়াই। সোজা কথা। সাফ কথা।’
লোকদুটো চলে যাবার পর সশব্দে দরজা লাগিয়ে আমি ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি মা দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন বিবর্ণ মুখে। বললেন, ‘কেন কইলি যে ধর্ম বিশ্বাস করি না! এখন তো ওরা আরও অসুবিধা করব।’
‘করুক।’ বলে আমি সরে আসি।
বিছানার তিন তোশকের তল থেকে মা লজ্জা বইটি বের করে রান্নাঘরে নিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, ‘কোনও দরকার নাই এই বই থাকার। কখন আবার এই বই আছে বইলা বাড়ির সবাইরে বাইন্ধা নিয়া যায়!’ আমার কমপিউটারে বইটি লেখা আছে। ছিঁড়ে ফেলা বইটির জন্য আমার মায়া হয় না। বরং একদিক দিয়ে ভাল। অযথা হয়রানি থেকে হয়ত বাঁচব।
আপদ বিদেয় হয় ঠিক কিন্তু সম্পূর্ণ বিদেয় হয় না। মিটিমিটি প্রায়ই ফোন করেন। আমি কেমন আছি, কেমন চলছে জীবন ইত্যাদি জিজ্ঞেস করেন। তিনি যে আমার মঙ্গল চান, এ কথাটি একবার একফাঁকে বললেন। মঙ্গল যেদিন চেয়েছেন সেদিনই জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কি আজকাল পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ধর্ম নির্মূল হোক, বিবাহ নির্মূল হোক?’
‘হ্যাঁ বলেছি। তাতে কি হয়েছে?’আমার কঠিন কণ্ঠ।
‘হোম মিনিস্ট্রি থেকে ব্যপারটি তদন্ত করতে বলেছে।’
আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোন রেখে দিই। আমি কোথায় কি বলেছি, তারও তদন্ত হয়! আমি কি বলব না বলব, কি লিখব না লিখব, সবকিছুর জন্য একটি সীমানা তৈরি করতে চাইছে তারা। সীমানার বাইরে বেরোলে তদন্ত হবে। মন্ত্রণালয়ে ফাইল খোলা হবে। ফাইলের পেট দিন দিন মোটা হতে থাকবে। পুলিশ আমাকে চোখে চোখে রাখে। সাদা পোশাকের পুলিশের লোক আর যে কোনও অপুলিশ আমার চোখে একই রকম দেখতে লাগে। কিন্তু আমি না বুঝলেও অন্যরা আমাকে বলে যে আমার বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করে টিকটিকিগুলো। কী চায় তারা, কী পায় তারা আমি জানি না।
শান্তিবাগ থেকে শান্তিনগরে এসে আমার মনে হয়েছিল একটু বোধহয় শান্তি জুটবে এবার। কিন্তু পুলিশের লোকেরা আমি যেখানেই যাই, সেখানেই ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করে। পুলিশই যদি কেবল সমস্যা হত, তাহলেও কথা ছিল। এ বাড়িতে ঢোকার পর থেকে নতুন নতুন সব উপদ্রব শুরু হয়েছে। কদিন পর পরই দরজার কড়া নড়ে, সমিতির টাকা দিতে হবে। আমি কোনও সমিতি করব না, জানিয়ে দিই, সুতরাং চাঁদা টাদা দেবার প্রশ্ন ওঠে না। মালিক-সমিতির লোকেরা জানান, সমিতির চাঁদা দিতেই হবে। এ থেকে মুক্তি নেই। বিশাল বড় চারটে দালান এই কমপ্লেক্সে। এক একটি দালান দশ তলা করে। চল্লিশটি করে আ্যপার্টমেন্ট এক দালানেই। একশ ষাটটি পরিবার, যা তা কথা নয়। সমিতির প্রয়োজন আছে। চুরি ডাকাতি বন্ধ করা, চব্বিশ ঘন্টা নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা করা, প্রহরীদের বেতন দেওয়া, আজ যদি লিফট নষ্ট হয়ে যায়, সারাবে কে? বাগানের মালি দরকার, কে যোগাবে? গাড়ির ড্রাইভারদের নাম ঠিকানা নথিভুক্ত করা, তেড়িবেড়ি করলে তাড়িয়ে দেওয়া, বারান্দাগুলো পরিষ্কার করা, ময়লা ফেলা ইত্যাদির জন্য লোক লাগানো, মাসে মাসে তাদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা, ডিশ আ্যণ্টেনা লাগানো, নষ্ট হলে সারানো, বাড়ির চামড়া খসে গেলে চামড়া বসানো, রং পুরোনো হলে নতুন রং করা, কাজের শেষ নেই। এসব তো আর ইস্টার্ন হাউজিং এসটেটের এর মালিক জহিরুল ইসলাম করবেন না, জহিরুল ইসলাম তো সব বাড়ি বিক্রিই করে দিয়েছেন। এসব ব্যবস্থাপনায় এখন তাদের থাকবে হবে, বাড়ি যারা কিনেছে। কিছু উৎসাহী মালিক মিলে এই সমিতি গঠন করেছেন। বছর গেলে নির্বাচন হবে সমিতির দাঁয়িত্ব কার কার কাঁধে পড়বে এ নিয়ে। সমিতির কাজ কেবল এসব সামলানো নয়। ভবিষ্যতেরও নকশা আছে। নিচে গ্যারেজের সামনে দোকান বসবে, লণ্ড্রি বসবে, বেকারি বসবে। মূলত, আমি বুঝি, পুরো এলাকাটির অর্থাৎ একশ ষাটটি আ্যপার্টমেণ্টের মানুষদের সুবিধের জন্য এই সমিতি। আমি মাসে মাসে বাঁধা বারোশ টাকার ব্যবস্থাটি মেনে নিই। একদিন সমিতির ঘরে ঢুঁ দিয়ে সেক্রেটারি শফিক আহমেদএর সঙ্গে পরিচিত হয়েও আসি। পরিচয় দেওয়ার আগেই তিনি বলে উঠলেন, চিনি আপনাকে। দেখেছেন কখনও আমাকে? জিজ্ঞেস করি। না, দেখিনি, তবে পত্রিকায় তো ছবি টবি সবসময়ই দেখি। সামনাসামনি এই প্রথম দেখলাম। একটি স্মিত হাসি ঝুলে থাকে মুখে, হাসির তলে এক টুকরো আশঙ্কা। আমাকে, আজকাল লক্ষ করছি, কোথাও নিজের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এটি কি ভাল, নাকি মন্দ! নিজেকে জিজ্ঞেস করি। মনে মনে নিজেকে উত্তর দিই, মন্দ।
এরপর সমিতি থেকে যে জিনিসটি করা হল, তা আমি সোজাসুজি বলে দিই, আমার দ্বারা হবে না। মসজিদের চাঁদা। মসজিদ বানানো হচ্ছে, এর জন্য আলাদা করে টাকা চাই। আমি বলি, আমার বাড়ি থেকে কেউ মসজিদে যাবে না, সুতরাং চাঁদা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তারপরও চাঁদা দিতে হবে। শফিক আহমেদ নিজে আসেন। সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট কালো জুতোর সাদাসিধে মাঝারি আকার ভদ্রলোক শফিক আহমেদ। একটি কলমের কোম্পানীর মালিক। কোম্পানির মালিক বলেই অঢেল সময় পান সমিতিতে ঢালার। মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন। আমার লেখাটেখা, বললেন, ভালই লিখি মাঝে মাঝে, বিশেষ করে দেশের স্বাধীনতা বিষয়ে যখন লিখি।
‘মসজিদের চাঁদা সবাই দিচ্ছে, আপনিও দিয়ে দেন। মসজিদ তৈরি হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ করতে টাকার দরকার।’
‘কমপ্লেক্সের ভেতরে মসজিদ করার দরকারটা কি? আশেপাশেই তো অনেক মসজিদ আছে। যারা নামাজ পরতে চায়, তারা ওইসব মসজিদে যেতে পারে।’
‘কিন্তু ভাই মসজিদ করার জন্য কমপ্লেক্সে আগে থেকেই প্ল্যান ছিল।’
‘অন্য যে কোনও কিছু তৈরি করতে টাকা লাগে নিয়ে যান। কিন্তু মসজিদ তৈরি করার জন্য আমি কোনও টাকা দেব না।
‘আপনার কী ক্ষতি, টাকা দিলে?’
‘লাভটা কি বলেন?’
‘লাভ না হোক। তবু তো সবার ব্যপার। আমাদের তো এখানে মিলেমিশেই থাকতে হবে। সবাই দিয়ে ফেলেছে টাকা,শুধু আপনারটাই বাকি আছে।’
‘আমার টাকার জন্য আপনাদের মসজিদ আটকে থাকবে না। আপনারা মসজিদ করতে চান করেন। আমি তো আপনাদের বাধা দিতে পারব না। কিন্তু মসজিদে আমি বিশ্বাস করি না, আমি কোনও টাকা মসজিদের জন্য দেবই না।’
শফিক আহমেদ চা খেয়ে বিদায় নেন।
এ করে যে শান্তি জুটবে তা নয়। সমিতি আয়োজন করছে মিলাদ মাহফিলের, চাঁদা দাও। দরজা থেকে বলে দিই, মিলাদে যাবো না, সুতরাং চাঁদা দেব না।
এরপর আবার। রোজার সময় ইফতারির আয়োজন হবে, চাঁদা দাও। ইফতারি খেতে যাবো না। চাঁদা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।
এরপর আরেকদিন। শবে বরাতের অনুষ্ঠান হবে। সেটির জন্য চাঁদা চাই। বড় একটি না বলে বিদায় দিই।
একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান হবে, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান হবে, চাঁদা দিয়ে দিই।
মসজিদের ঘটনার দু সপ্তাহ পর শফিক আহমেদের ফোন পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছ!, কায়সার কে?’
‘কায়সার? কেন? কায়সার আমার বন্ধু।’
‘আপনার বাড়িতে আসে নাকি প্রায়ই?’
‘হ্যাঁ আসে। কেন, কি হয়েছে?’
‘কথা হচ্ছে।’
‘কোথায় কথা হচ্ছে?’
‘সমিতিতে।’
‘কি কথা?’
‘বলছে আপনার সঙ্গে নাকি অবৈধ সম্পর্ক আছে কায়সারের।’
আমি জোরে হেসে উঠি। ‘আমার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক , সম্পর্ক বৈধ না অবৈধ তা দেখার কাজ সমিতির? সমিতিকে আমার শোবার ঘরে ঢোকার অনুমতি কে দিয়েছে?’
শফিক আহমেদ বললেন, ‘এসব তো আর আমি করছি না ভাই। আমি শুভাকাঙ্খী হিসেবে আপনাকে জানাচ্ছি। এগুলো করছেন ইস্টানং হাউজিংএর চিফ ইঞ্জিনিয়ার জুবাইর হোসেন, দুই নম্বর বিল্ডিংএ তাঁর আ্যপার্টমেন্ট আছে। সমিতির সভাপতি তিনি।’
‘যা ইচ্ছে করুক। যা ইচ্ছে বলুক। আমি পরোয়া করি না।’
‘আপনাকে মনে হয় চিঠি দেবে।’
‘কিসের চিঠি?’
‘কোনও অবৈধ কাজ যেন আ্যাপার্টমেণ্টে না করেন এ ব্যপারে চিঠি।’
‘আমার বাড়িতে আমি কি করি না করি, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যপার।’
আমি ফোন রেখে দিই। এসব বিষয়ে কথা বলার প্রবৃত্তি হয় না আমার।
এরপর আবারও এক রাতে ফোন। শফিক আহমেদ জানালেন সভাপতি উঠে পড়ে লেগেছেন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। তাঁর পক্ষে অনেকেই আছে। এও জানালেন, সমিতির অধিকার আছে কোথাও কোনও অবৈধ কাজ হচ্ছে কি হচ্ছে না তার খবর নেওয়া এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।
‘অবৈধ বলতে কি বোঝাচ্ছেন?’
‘ধরেন, কোনও বাড়ির মালিক যদি তার বাড়িটাকে প্রসটিটিউশনের কাজে ব্যবহার করে। এরকম তো হতে পারে। দেখা গেল বাড়িতে প্রসটিটিউট আর ক্লায়েন্ট এনে রীতিমত ব্যবসা করছে মালিক, তখন সমিতির দায়িত্ব সেই লোককে উচ্ছেদ করা।’
‘কি করে উচ্ছেদ করবেন বাড়ির মালিককে? বাড়ির মালিক তো তিনি।’
‘এরকম নিয়ম আছে। বাড়ি বিক্রি করে যেতে তিনি বাধ্য।’
‘আমি তো কোনও ব্যবসা করছি না আমার বাড়িতে। তবে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থার কথা বলছেন কেন তিনি?’
‘অবৈধ কাজ করছেন বলে তারা ভাবছে। আমি আপনার শুভাকাঙ্খী। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি কায়সারকে বলে দিন আপনার বাড়িতে না আসার জন্য।’
আমি রুখে উঠি। ‘না, আমি তা বলব না। এখানে কায়সার কোনও ব্যপার না। আমার বাড়িতে কে আসবে না আসবে, কে থাকবে না থাকবে, কে ঢুকবে বাড়িতে, কে বাড়ি থেকে বেরোবে, সেটা সম্পূর্ণ আমার সিদ্ধান্তে হবে। সমিতির সিদ্ধান্তে না। এ আমার শেষ কথা। এটা হচ্ছে মানুষের একটা মিনিমাম ফ্রিডম। এই ফ্রিডম আমি বিসর্জন দেব না।’
‘তাহলে চিঠি পাঠাবে।’
‘পাঠাক।’
‘প্রথম ওয়ার্নিং। তারপর সেকেণ্ড ওয়ার্নিং। থার্ড। তারপর বোধহয় বাড়িছাড়ার আদেশ।’
‘যা ইচ্ছে করুক। আমার বাড়ি থেকে আমাকে উচ্ছেদ কী করে করে আমি দেখব।’
খটাশ করে ফোন রেখে দিই। শ্বাস পড়ছে দ্রুত আমার। নিজের কেনা বাড়ি, এই বাড়ি থেকে আমাকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র চলছে। কোনও ভাড়া বাড়িতে আমার স্থান হয় না, এখন যদি নিজের বাড়িতেও বাস করার অধিকার না থাকে আমার, তবে যাবো কোথায়! আমার তো পেছোতে পেছোতে পেছোবার আর কোনও পথ নেই। ঠেলতে ঠেলতে লাথি কষাতে কষাতে আর কোথায় আমাকে নিতে চায় মানুষ! আর কত সর্বনাশ ঘটাতে চায় আমার! অস্থির হাঁটাহাঁটি করি ঘরে বারান্দায়। বাড়িটি কেনার পর নিজে হাতে সাজিয়েছি। রান্নাঘরের দেয়ালগুলোয় নিজে পছন্দ করে টাইলস কিনে এনে লাগিয়েছি, পুরো আধুনিক কেবিনেটে সাজিয়ে দিয়েছি রান্নাঘরটি, বড় শ্বেত পাথর বসিয়েছি কাটা বাছা করার জায়গায়, ভারি পর্দা কিনে সবগুলো জানালায় টাঙিয়ে দিয়েছি, পর্দাগুলো দেয়ালের মাথা থেকে মেঝে পর্যন্ত, কাঠের সোফা কিনেছি বৈঠক ঘরের জন্য, শোবার ঘরে নতুন একটি খাট পেতেছি, নতুন একটি বড় সেগুন কাঠের আলমারি বসিয়েছি, লেখার ঘরটির চারদেয়াল জুড়ে রেখেছি বইয়ের আলমারি, আলমারি ভর্তি বই, টেবিলে কমপিউটার। নিজের বাড়ি, নিজের সাধ্য মত রুচি মত সাজিয়ে বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিমন্ত্রণ করে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান করেছি। অস্থির জীবনটি শেষ পর্যন্ত একটি নিশ্চিন্তের জায়গায় এসে স্থির হয়েছে। স্বামী ছাড়া কোনও মেয়ের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, আমার পক্ষেও সম্ভব হবে না, একা কোনও মেয়ে পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাওয়া অসম্ভব ইত্যাদি বাণীকে আমি মিথ্যে প্রমাণ করেছি। গুষ্ঠির মধ্যে কেউই যা করতে পারেনি, তা আমি করে দেখিয়েছি যে মেয়ে হয়ে আমি তা করতে পারি। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমি যখন ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েছি, তখন কি না আমাকে আমার বাড়ি থেকেই তাড়িয়ে দেবে! কোথায় কোন নর্দমায় আমাকে ফেলতে চাইছে মানুষ! আমার মরণ না দেখে কারও বুঝি স্বস্তি নেই! সমাজে বাঁচতে হলে সমস্ত স্বাধীনতার গলা টিপে ধরে বাঁচতে হবে! আমার নিজস্ব কোনও মূল্যবোধ নিয়ে আমার বেঁচে থাকার অধিকার নেই! ক্রোধ আমার সর্বাঙ্গে। হাত নিশপিশ করে, মুহূর্তের জন্য মনে হয় একটি যদি রিভলভার পেতাম কোথাও, নির্দ্বিধায় আমি খুন করতে পারতাম জুবায়ের নামের লোকটিকে।
জুবায়ের হোসেন আমাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করেন। তাঁর বাড়ি এক নম্বর দালানে নয়, তারপরও এক নম্বরের লিফটে চড়তে গেলেই ধোপ দুরস্ত ধবল শার্দূলটির শ্যেনচক্ষুদুটি দেখি সামনে। একদিন কায়সার আর আমি সেই একই লিফটে, তিনিও। আমাদের দেখে রোষে তাঁর নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছিল। সেদিনই কায়সার তার গাড়ি রেখেছে অতিথির গাড়ি পার্কিংএ। জুবায়ের হোসেন দাঁড়িয়েছিলেন, কায়সারকে বললেন গাড়ি সরিয়ে নিতে, কারণ ওটি নাকি ঠিক জায়গা নয় গাড়ি রাখার। কায়সার বলল, ‘কেন, এইখানে তো জায়গা খালি আছে, গাড়ি রাখলে অসুবিধা কী?’
‘অসুবিধা আছে।’ নিরাপত্তা প্রহরীরা জুবায়েরের ইঙ্গিতে কায়সারকে জানিয়ে দেয়।
‘কি অসুবিধা, বলেন।’
জুবায়ের চেঁচিয়ে বললেন, ‘আপনার গাড়ি এইখানে পার্ক করা যাবে না।’
‘কেন যাবে না?’ কায়সারের স্বরও উঁচুতে ওঠে।
‘দেখে নেব, ঠিক আছে আমিও দেখে নেব’ ধরণের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলে দুজনের মধ্যে। কায়সারকে শেষ পর্যন্ত গাড়ি সরিয়ে রাস্তার কিনারে রেখে আসতে হয়।
কায়সারের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা ধারণ করেন জুবায়ের হোসেন। কায়সারকে অপমান করার অর্থ আমার অতিথিকে অপমান করা, আমার অতিথিকে অপমান করার অর্থ আমাকে অপমান করা। জুবায়ের হোসেন আমাকে আমার বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। না, তারপরও মসজিদের চাঁদা আমি দিই না, কায়সারকে আমার বাড়ি আসতে আমি বারণও করি না।
মা আমাকে বলেন, ‘তুই যে এমন হুট কইরা চাকরি ছাইড়া দিলি, এখন কি হইব? টাকা পয়সা যা ছিল সব দিয়া ত বাড়ি গাড়ি কিনছস।’
‘বাড়ি গাড়ি কি সাধে কিনছি? উপায় ছিল না বইলাই ত কিনছি।’
‘এখন চাকরি না থাকলে চলবি কি কইরা?’
‘সেইডা তোমার চিন্তা করতে হবে না।’
মার উদ্বিগ্ন মুখের সামনে থেকে সরে আসি বটে, এই দুশ্চিন্তা কিন্তু আমাকে শকুনের ডানার মত ঢেকে ফেলেছে। কোনও প্রকাশক এখন আমাকে কোনও টাকা পয়সা দেবেন না। কারও কাছে কোনও রয়্যালটির টাকা বাকি পড়ে নেই। বরং আমিই দায়বদ্ধ সবার কাছে। বই লিখে তাঁদের টাকা শোধ করতেই আমার কয়েক বছর লেগে যাবে। বই তো আমি দুদিনে বসে লিখে ফেলতে পারি না। তার ওপর জোর করে নিজেকে দিয়ে আমি লেখাতেও পারি না। যদি না ভেতরে তোলপাড় হয়ে কিছু বেরিয়ে আসে। বসন্তের কুঁড়ি যেমন আপনিতেই ফুল হয়ে ফোটে, তেমন করে ফুটতে হয় আমার শব্দকে। আমি জোর করে ধমক দিয়ে কান মলে বাক্য রচনা করতে পারি না। আসলে আমি তো লেখক নই। যা লিখেছি এতদিন, তা না লিখে আমি পারিনি বলেই লিখেছি। লিখতে গিয়ে আমি কাঁদি। কোনও নারীর দুঃখের কথা লিখছি, লিখতে লিখতে দুঃখিতাটির জন্য অঝোরে কাঁদছি আমি, আমি অনুভব করতে থাকি সেই দুঃখিতা নারীটি আমি নিজে। ফেরা লিখতে গিয়ে চোখ আমার ঝাপসা হয়ে উঠেছে বার বার, নিজেকে আমার মনে হয়েছে আমিই কল্যাণী। কখনও কখনও কষ্ট এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে আমি লেখা ছেড়ে উঠে যাই, বিছানায় গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদি। যখন নিমন্ত্রণ নামের উপন্যাসটি লিখেছি, আমি অনুভব করেছি আমি সেই বালিকা, প্রেমিক যাকে নিমন্ত্রণ করেছিল, যাকে প্রেমিকসহ সাতজন পুরুষ উপুর্যুপরি ধর্ষণ করেছে। আমি কঁকাতে কঁকাতে, ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে সেই ধর্ষণের বর্ণনা করেছি, যেন আমাকেই ধর্ষণ করা হচ্ছে, যেন আমারই যৌনাঙ্গ ছিঁড়ে রক্তের ফিনকি ছুটছে। আমি সত্যি সত্যিই যন্ত্রণা অনুভব করেছি আমারই যৌনাঙ্গে। লিখে শেষ করে, যখন বালিকাটি তার বাড়ির দিকে যাচ্ছে, যাচ্ছে আর ভাবছে, বাড়ি ফিরলে যখন তার বাবা জিজ্ঞেস করবেন, কোথায় গিয়েছিলি? সে তখন একটুও মিথ্যে বলবে না, বলবে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। এটুকু লিখে আমি হু হু করে লেখাটির ওপর উপুড় হয়ে কেঁদেছি। অপরপক্ষে যখন যমুনার গল্প লিখছি, লিখতে লিখতে আমি নিজেই যমুনার অস্তিত্ব অনুভব করি আমার ভেতর। যমুনা যখন সন্তান ধারণ করছে এবং ঘোষণা করছে এ তার সন্তান, অন্য কারও নয়, কোনও পুরুষের নয়, তখন আমারই মনে হয় যেন আমিই অন্তসত্ত্বা, আমারই ভেতর বেড়ে উঠছে আমার সন্তান, বিবাহবহির্ভূত সন্তান, যে সন্তানটিকে ভালবেসে বেড়ে উঠতে দিচ্ছি। শোধ গল্পটি লেখার সময় আমি নিজে ঝুমুর হয়ে স্বামী আফজালের ওপর শোধ নিই, গল্পটি লিখে একটি তৃপ্তির হাসি আমার ঠোঁটের কোণে অনেকক্ষণ লেগে থাকে, যে তৃপ্তি ঝুমুর পেয়েছিল, সেই তৃপ্তি। ভ্রমর কইও গিয়া বইএর গল্পটিতে নরাধম নপুংসক স্বামীর সংসার থেকে চলে গিয়ে সকলের ভ্রূকূটি তুচ্ছ করে একা একটি মেয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে, নিজেকে আমার মনে হয়েছে আমি সেই মেয়ে। আমি লেখক নই। ছটা বারোটার নিয়ম করে আমি লিখতে পারি না। আমাকে বসতে হবে লিখতে, এমন কোনও অনুরোধ বা আদেশ আমাকে লেখার জন্য বসাতে পারেনি। অবশ্য অনেক কলাম লিখেছি যেন তেন করে, কিছু ফরমায়েসি লেখা, কিছু লেখা অভাবে পড়ে, না লিখে উপায় ছিল না বলে লেখা। প্রাণ খুঁজে পাইনি ওসব লেখায়। যেহেতু লেখক নই, আমার বাক্যগঠন সঠিক হয় না, আমার বানান গুলো শুদ্ধ হয় না, যেহেতু লেখক নই, গুছিয়ে কোনও ঘটনার বর্ণনা করতে পারি না। আমি জানি আমার সীমিত জ্ঞানের খবর। গ্রামের কোনও কৃষককে ধরে এনে কোনও লোহালককরের কারখানায় কাজ করার জন্য ছেড়ে দিলে যেমন অবস্থা হবে, আমার অবস্থা অনেকটা সেরকম মনে হয় লেখার জগতে। লেখক হওয়ার যোগ্য আমি নই তারপরও লেখক হিসেবে আমার পরিচয়। এই পরিচয়টি ধীরে ধীরে গৌণ থেকে মুখ্য হয়ে উঠেছে। এখন আর অবসরে শখের লেখা লেখার লেখক নই আমি। বিশেষ করে যখন লেখার জন্য এত বছরের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি। লেখক পরিচয়টিকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব, এখন তার আর উপায়ও নেই।
বাড়ি কিনেছি, বাড়িভাড়া দিতে হয় না, খরচ কমার কথা! কিন্তু হিসেব করে দেখি খরচ আরও বেড়েছে। বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, গ্যাসবিল, সমিতির বিল, ড্রাইভারের বেতন সব মিলিয়ে অনেক। দুশ্চিন্তার চাদরটি, আমি না চাইলেও আমাকে ঢেকে রাখে। মা সেই আগের মতই আমার খরচ বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কী দরকার ওই সামান্য কিছু জিনিস ময়মনসিংহ থেকে এনে বাবার সাহায্য ছাড়া আমার গতি নেই ধরণের কোনও একটি মিথ্যেকে সুযোগ দেবার কখনও কারও মুখে উচ্চারিত হতে! মাকে বলেছি। বলেও মার এই স্বভাবটি দূর করতে পারিনি। সেদিনও দেখি ময়মনসিংহে গিয়ে বাবাকে অনুরোধ উপরোধ করে অনেকটা চেয়ে ভিক্ষে করে নিয়ে এসেছেন কিছু জিনিস। নান্দাইলের জমি থেকে যে চাল আসে অবকাশে, সেই কিছু চাল, এক বোতল সয়াবিন তেল, কিছু পেঁয়াজ, রসুন। গামছায় বেঁধে দু তিন সের মসুরির ডালও এসেছেন। দুটো লাউ, কিছু পটল, চারটে গাছের নারকেল। সেদ্ধ হওয়া গরমে বাসে করে যাওয়া আসা! ঘামে মার সারা শরীর আঠা আঠা হয়ে আছে। শাড়ি লেপটে আছে আঠার সঙ্গে। আমি দেখি, সেদিন আর বলি না, বলি না যে খামোকাই এনেছেন মা এগুলো। কোনও কোনও সময় সামান্য কিছুই খুব বড় কিছু বলে মনে হয়। কিন্তু কারও করুণায় আমার বাঁচবো কেন! অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙছে, টের পাচ্ছি। সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিলে তো আমার ডাক্তারি বিদ্যেটি সেই ইস্তফার সঙ্গে চলে যায়নি কোথাও। তাই প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোয় ধর্না দিতে থাকি, কোনও ডাক্তার তাদের লাগবে কি না জিজ্ঞেস করি। ডাক্তার লাগবে। মাত্র পাশ করে বেরোচ্ছে এমন অদক্ষ ডাক্তারদেরও তারা নিচ্ছে। আমাকে লুফে নেওয়ার কথা। স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগ এবং আ্যানেসথেসিয়া বিভাগে ঢাকা শহরের বড় দুই সরকারি হাসপাতাল মিটফোর্ড আর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমার দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা শুনে প্রাইভেট ক্লিনিকের ব্যবস্থাপকদের চোখ সোনা পাওয়া খুশিতে নেচে ওঠে। এরপর যে কাজটি তাঁরা করেন, আমার নাম জিজ্ঞেস করেন। নাম শুনে সকলেই পাংশু মুখে বলেন, আপনার নাম ঠিকানা অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কাগজে লিখে রেখে যান অথবা চাকরি চেয়ে লিখিত আবেদন করুন, কমিটির বাকি সদস্যের সঙ্গে কথা বলে আমরা আপনাকে খবর দেব। সে খবর পাওয়া আমার আর হয়ে ওঠে না। আমার নাম দেখেই বাতিল করা হয় আমাকে। ডাক্তারের প্রয়োজন হলেও আমাকে প্রয়োজন হয় না কারওর। আমি একটি বাতিল নাম। আমি একটি নিষিদ্ধ নাম।
ইয়াসমিন অনেকদিন থেকে বলছে ওর জন্য যেন একটি চাকরি যোগাড় করে দিই। শুধু বলছেই না, কাঁদছে। কি করে চাকরির যোগাড় করি ওর জন্য! উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ভাল নম্বর পেয়ে অনার্স সহ মাস্টার্স পাশ করা মেয়ের কোনও চাকরি নেই এ দেশে। ঢাকার ইশকুল কলেজগুলোয় উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষিকা হওয়ার আবেদন করেছে, কাজ হয়নি। ওসব জায়গায় ঢুকতে হলে ওপরঅলাদের কৃপা থাকতে হয়। আমাদের ওপরঅলা নেই, মামা চাচা থাকতে হয়, তাও নেই। ইয়াসমিন মন খারাপ করে বসে থাকে। আমার সঙ্গে অনেক লোকের আলাপ আছে ভেবে আমার ওপর নির্ভর করে থাকে ওরা, ইয়াসমিন, মিলন। মিলনও বলছে আদমজী জুট মিলের ওরকম মাছি মারা কেরানির চাকরি ওর ভাল লাগে না। আমি যদি ওর জন্যও ভাল একটি চাকরির ব্যবস্থা করি। কিন্তু আমার নিজের চাকরি খেয়েই নিজে বসে আছি, ওদের জন্য আর কতটা কি করতে পারব! নিজের যেহেতু ক্ষমতা নেই, কাছের দুএকজন মানুষকেই বলি যদি কারও পক্ষে সম্ভব হয় কিছু করা।
দীর্ঘদিন বলার পর খিরাজখোর কায়সার শেষ পর্যন্ত ইয়াসমিনের জন্য একটি চাকরির খবর দেয়। কায়সার যে কখনও কোনও চাকরির খবর দিতে পারবে, তা আমার ধারণা ছিল না কারণ কথা সে যে কোনওকিছুতে দিয়ে দেয়, নিরানব্বইভাগ কথা সে রাখে না অথবা রাখতে পারে না। বলল কাল সকালে সে আসবেই আসবে, কাল সকাল গিয়ে পরশু সকাল পার হয়, তার দেখা নেই, সপ্তাহ পার হয়, নেই দেখা, দশদিন পর ভর সন্ধেয় হয়ত উদয় হয়। সুতরাং কায়সার কথা দিল যে সে চাকরির খোঁজ করবে, কিন্তু তার ওপর আমাদের কারওরই সত্যিকার ভরসা থাকে না। আর চাকরির খোঁজ দিলেও কেমন ধরণের চাকরি সেটি, তা মোতালেবের চাকরিটি দেখেই অনুমান করা গেছে। সেই যে রুটি বানানোর কারখানায় কাজ দিয়েছিল, মোতালেব সেখানে সাতদিনও টিকতে পারেনি। চোখের সামনে তাকে প্রতিরাতে দেখতে হত কারখানার মালিক মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কোনও কারণ ছাড়াই শ্রমিকদের বেধড়ক পেটাচ্ছে। মোতালেব তল্পি তল্পা গুটিয়ে চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে। কায়সারের ওপর ভরসা না করলেও সে ঠিক ঠিকই চাকরির খবরটি দেয়। অবশ্য খুব জোরে সোরে দেয় না, কারণ সে নিশ্চিত যে এই চাকরি কারওরই পছন্দ হবে না। বলার পরই নাকচ হয়ে যাবে। চাকরির বৃত্তান্ত শুনে আমি কায়সারকে বলে দিই, ‘অসম্ভব। এই চাকরি করা যাবে না। অন্য কোনও চাকরি পাওয়া যায় কি না দেখ, যেখানে ও তার বোটানির জ্ঞানটা কাজে লাগাতে পারে।’ চাকরিটি ইয়াসমিনেরও পছন্দ হওয়ার কথা নয়। একটি বস্ত্রকল ব্যবসায়ীর প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি। কি কাজ ওখানে? ফোনে কথা বলবে, মালিক আপিসে আছে কি না নেই এই খবর দেবে লোককে, আর আপিসের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখবে। এই করার জন্য এতগুলো বছর ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান পড়েছে! কিন্তু আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ইয়াসমিন বলে, ‘যে রকমই হোক, আমি করব চাকরি।’ অসহায় তাকিয়ে থাকি বোনটির দিকে।
মিলনও বলে, ‘ও করুক চাকরি বুবু। আজকাল কি আর যে বিষয়ে পড়ালেখা করে মানুষ, সেই বিষয়ে চাকরি পায়? কেমেস্ট্রিতে মাস্টার্স কইরা ব্যাংকের একাউনটেন্ট হইতাছে না? ফিজিক্সে পড়ছে আমার এক বন্ধু, কোথাও চাকরি নাই। শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসার টিচার হইছে। বাংলা সাহিত্যে এম এ পাশ পইড়া কারখানার সুপারভাইজারের পদে কাম লয়। মানুষ করবে কি বুবু? চাকরি ত নাই। তাই যেইডাই পায়, সেইডাই করে। আপাতত করতে থাকুক, পরে ভাল চাকরি পাইলে এইটা ছাইড়া দিবে।’
আমার চাকরি নেই। ইয়াসমিন তার স্বামী সন্তান নিয়ে আমার বাড়িতে থাকে। মিলন যে টাকা উপার্জন করে তার প্রায় সবটাই বাচ্চার খরচে চলে যায়। ওদের আর কোনও বাড়তি টাকা নেই যে সংসার খরচে সাহায্য করবে। এরকম জীবন ইয়াসমিনকে যন্ত্রণা দেয় তাই যেমনই চাকরিটি, এ সময় যে কোনও চাকরিই যেহেতু সোনার হরিণের মত, লুফে নেয়। চাকরিটি করতে ও সকালে বেরিয়ে যায়, বিকেলে ফেরে। দু হাজার টাকা মাসের শেষে। এ অনেক টাকা ওর কাছে। একদিন লক্ষ করি, ইয়াসমিন আপিসে যাওয়ার সময় খুব সাজে। কড়া কড়া রঙের শাড়ি পরে, চোখে খুব কালো করে কাজল পরে, ঠোঁটে কড়া লাল লিপস্টিক লাগায়। দেখে আমার ভাল লাগে না। বলি, ‘অত সাজস কেন?’
ইয়াসমিন উত্তর দেয়, ‘কেন, সাজলে অসুবিধা কি?’
‘না সাজলে অসুবিধা আছে তর?’
‘সবাই সাজে, তাই আমিও সাজি।’
‘তুই তো আগে এইরম ভূতের মত সাজতি না। এহন কি হইছে তর?’
‘কিছু হয় নাই। আমার সাজা নিয়া তোমার ভাবতে অইব না।’
ইয়াসমিন গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে যায়। একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আমি দিশেহারার মত দাঁড়িয়ে থাকি। আমি বুঝি, ইয়াসমিন ওর চাকরিটি টিকিয়ে রাখতে চাইছে সেজে। প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজে কোনও মেধার দরকার হয়না, যে মেধাটি ওর আছে। দরকার হয় রূপের। সেই রূপ যে ওর আছে অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারি হওয়ার যোগ্যতা যে ওর আছে তা প্রকট করে ওর আপিসের লোকদের দেখাতে চাইছে। যেন আপিসের কেউ কুরূপা কুচ্ছিত বলে ওকে ছাটাই করার কথা ভাবতে না পারে।
২৩. ফতোয়া
দেশ জুড়ে চলছেই আমার মুণ্ডুপাত। এমন কী অবকাশের বাউণ্ডারি ওয়ালে পোস্টার পড়েছে, আরোগ্য বিতানের দেওয়ালেও। ‘তসলিমা নাম্নী এক কুলটা কুলাঙ্গার, যৌনাচারী পাপাচারী, ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন।’ যেন মজার বিষয়। তসলিমাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছে রঙ্গ করা যায়। এতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। বাধা কে দেবে, আমি তো কোনও দল করি না যে আমার দলের লোক গিয়ে ওদের মাথাটা ফাটিয়ে আসবে। এমন সময় খবরটি বেরোয়, প্রকাশ্য জনসভায় সিলেটের সাহাবা সৈনিক পরিষদের সভাপতি মাওলানা হাবীবুর রহমান আমার মাথার মূল্য ঘোষণা করেছেন। মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা। আমার মাথাটি কেটে নিয়ে হাবীবুর রহমানের হাতে যে দেবে, সে পাবে এই টাকা। পঞ্চাশ হাজার টাকা নেহাত কম টাকা নয় বাংলাদেশে। প্রথম মোটেও আমি গা করিনি। প্রতিদিন তো কতই খবর বেরোচ্ছে আমার বিরুদ্ধে। বাংলাবাজার পত্রিকার এই খবর আর এমন কি সত্য! মতিউর রহমান চৌধুরী অনেকদিন থেকে লেগে আছেন আমার পেছনে। খবরটি নিশ্চয়ই তিনি বানিয়ে লিখেছেন। পত্রিকাটি পত্রিকার জায়গায় রেখে নিজের কাজে মন দিই। এর ঘণ্টাখানিক পর পত্রিকাটি নিয়ে আবার খবরটি পড়ি। সিলেটের লোক মতিউর রহমান চৌধুরী, সিলেটের খবরাখবর অন্যান্য সাংবাদিকদের চেয়ে তিনি বেশি জানেন। ফতোয়ার খবরটি তিনি প্রথম পাতায় একটি চারকোনা বাক্সের মধ্যে ছেপেছেন। না, এ কোনও উড়ো খবর নয়, প্রথম পাতায় ছাপা হওয়া গুরুত্বপূর্ণ খবর। হঠাৎ আমার বুকের মধ্যিখানটায় অনুভব করি হিম হিম কিছু। আন্দোলন হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে, মসজিদে প্রতি শুক্রবার আমাকে গালিগালাজ করা হয়, লিফলেট বিতরণ হয়, পোস্টার ছাপা হয়, দেয়ালে সাঁটা হয়, মিছিল মিটিংএ আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছে, ওয়াজ মাহফিলে, ইসলামি জলসায় আমার চিবিয়ে খাওয়া হচ্ছে, হচ্ছে হোক, সবারই গণতান্ত্রিক অধিকার যাকে খুশি গাল দেওয়া, কিন্তু মাথার মূল্য ধার্য হবে কেন! এ অধিকার কে কাকে দিয়েছে!
আমার ফাঁসির দাবিতে মাওলানা হাবীবুর রহমান সিলেট শহরে অর্ধ দিবস হরতাল ডেকেছেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম, কোথাকার কোন সাহাবা সৈনিক পরিষদের ডাকে হরতাল হবে না। কোনও বড় রাজনৈতিক দল ছাড়া হরতালের ডাক দিলেই তো আর হরতাল হয় না! কিন্তু আমাকে অতিবিস্মিত হতে হয়, যখন খবর বেরোয় যে অতি শান্তিপূর্ণভাবে সিলেট শহরে অর্ধ দিবস হরতাল পালন হয়েছে। শহরে কোনও দোকান পাট খোলেনি, গাড়ির চাকা ঘোরেনি। কী কারণ হরতাল পালনের! কারণ সিলেটের মানুষ আমার ফাঁসি চায়। ফাঁসি যদি সরকার না কার্যকর করে, তাতে ওদের অসুবিধে নেই। মাথার মূল্য ঘোষণা করা আছে। যে কেউ মাথাটি কাটার ব্যবস্থা করতে পারে। ঘরের গা- কাঁপা আঁধারে আমি রুদ্ধশ্বাস বসে থাকি। জানালা দরজার পর্দা টেনে দেওয়া, যেন বাইরে থেকে কেউ আমাকে লক্ষ করে গুলি না ছোঁড়ে। এই ব্যবস্থায় যে কাজ হবে না, তা আহমদ শরীফ বলেন। তিনি আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী করছেন?’
‘কিছু না, বসে আছি।’
আহমদ শরীফ ধমক লাগালেন, ‘বসে থাকলে হবে? কী কাণ্ড হচ্ছে, টের পাচ্ছেন না! এক্ষুনি পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেন।’
‘পুলিশ পাহারা? কি করে করব?’
‘মতিঝিল থানায় একটি চিঠি লিখে দেন। লেখেন যে আপনার মাথার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং আপনার জন্য যেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। আমি লোক পাঠাচ্ছি, আমার লোক আপনার চিঠি নিয়ে থানায় দিয়ে আসবে।’
আহমদ শরীফ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তাত্ত্বিক সাহিত্যিক, ধর্মের কঠোর সমালোচক, তাঁর ফাঁসির দাবিতেও মোল্লারা একসময় পথে নেমেছিল। আহমদ শরীফ জানেন যে মোল্লার দৌড় কেবল মসজিদ পর্যন্ত নয়। তাঁর বাড়িতে যে সাপ্তাহিক আলোচনার আসর বসে ধড়িবাজদের ধর্মের ধড় ধসিয়ে দেবার, ওতে অংশ নিতে আমাকে একবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গিয়েছিলাম। কিছু কিছু বিজ্ঞ বিদগ্ধ মানুষ আছেন, যাঁদের বিরাটত্বের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া পেলে, যাঁদের বিচ্ছ.রিত বিভায় স্নাত হতে পারলে সমস্ত বিভ্রান্তি বিদায় হয়। আহমদ শরীফের মত এমন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির প্রশ্রয় আমাকে প্রসন্ন করে। গজনবী নামের এক লোককে পাঠালেন আহমদ শরীফ। গজনবী আমার নিরাপত্তা চাওয়ার চিঠি মতিঝিল থানায় দিয়ে এলেন। এরপর দুদিন যায়, তিনদিন যায়, সপ্তাহ চলে যায়, থানার লোকেরা মোটেও রা শব্দ করেন না। কোনও নিরাপত্তা রক্ষীর টিকিটি দেখতে পাওয়া যায় না। সকাল বিকাল হাত পা ঠাণ্ডা হচ্ছে। বাড়িতে বলে দিয়েছি কোনও অচেনা কেউ এলে যেন দরজা কেউ না খোলে। নিচে দারোয়ানদেরও বলা আছে ইন্টারকমে যেন কথা বলে নেয় কেউ আমার খোঁজে এলে। এখানকার নিয়মই এই, তারপরও বিশেষ ভাবে সচেতন থাকার জন্যও অনুরোধ করি। কি কারণ এই বাড়তি সতর্কতার তা অবশ্য ভেঙে বলি না। ভাল যে বাড়ি কেনার পর পরই একটি গাড়ি কিনে ফেলেছিলাম, এখন আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খোলা রিক্সায় চড়তে হয় না। চড়ে অনেক ধেয়ে আসা লোকের তারস্বরে চিৎকার শুনেছি।
ওই দেখ দেখ তসলিমা যায়।
মাগীরে দেখ। মাগীরে দেখ।
ওই ধর ধর।
টাইন্যা নামা রিক্সা থেইকা। ধোলাই দে।
নাস্তিক যায় রে নাস্তিক যায়।
ওই খানকি!
এসব অনেক শোনা হয়েছে। আর কত! যে কোনও সময় আমাকে রিক্সা থেকে নামিয়ে শেয়াল শকুনের মত খুবলে খেয়ে ফেলতে দ্বিধা করত না ওরা। গাড়িতে চড়ে কোথায়ই বা আমার যাওয়া চলে! কোনও দোকানে! কোনও মেলায়! কোনও অনুষ্ঠানে! নাটক সিনেমা দেখতে! কোনও পার্কে! কোনও সভায়! না। কোথাও না। কোথাও আমার যাওয়া চলে না। আমি বুঝে ওঠার আগেই আমার চলাচলের সীমানা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে উঠল। আমি বুঝে ওঠার আগেই আমি ঘরবন্দী হলাম। কবিবন্ধুরাও আমাকে কোথাও আর আমন্ত্রণ জানান না। কবিতার অনুষ্ঠান থেকে কবিতা পড়ে এসে জানান অনুষ্ঠান চমৎকার হয়েছে। লেখকদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে, অনুষ্ঠান শেষে জানান কেমন হল, কী হল। শিল্পী সাহিত্যিকদের র্যালী হচ্ছে, র্যালী থেকে ফিরে এসে জানান কেমন জমজমাট হয়েছে সে র্যালি। সকলে ব্যস্ত উচ্ছল উৎসবে, মৌসুমি মেলায়, মঞ্চে। নাটক হচ্ছে, গান হচ্ছে। সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছে। কেউ একবার দুঃখ করেন না আমার জন্য, আমি যে যেতে পারিনি। আমি যে যেতে পারব না, এটি যেন চিরন্তন সত্য। হঠাৎ যদি কোনওদিন বলে বসি, আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে। তখন চমকে ওঠেন বন্ধুরা, বলেন, ‘বল কি বল কি, পাগল নাকি তুমি! বাইরে বের হয়ো না। কখন কি বিপদ হয় বলা যায় না।’ সুতরাং নিরাপদে থাকো। ঘরে বসে থাকো চুপটি করে। লক্ষ্মী মেয়ের মত। আমরা আনন্দ করে বেড়াবো। আমরা হৈ হল্লা করব। তোমার জন্য এসব নয়। নিরাপত্তা তোমার জন্য জরুরি। আনন্দ স্ফূর্তি নয়। উৎসব নয়। ঘরে বসে থাকতে মন খারাপ লাগে? কিন্তু বেঁচে তো আছো। বেঁচে থাকাটা প্রয়োজন। কথা ঠিক বটে। কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকতে কেমন লাগে তা সম্ভবত কেউই অনুমান করতে পারেন না। তবে ওঁরা আসেন আমার বাড়িতে। আমিও যাই মাঝে মাঝে ওঁদের বাড়িতে। বাড়িতে বাড়িতে আমাদের দেখা হয়। ওঁরা যখন আসেন, খানিকটা ভয়ে ভয়েই আসেন, এসবির লোকদের ভয়। আমার বাড়িতে আসা মানে সরকারি খাতায় নথিভুক্ত হয়ে যাওয়া ওঁদের নাম ঠিকানা। নিচে নিরাপত্তা প্রহরীর ঘরে খাতায় নাম লিখে আসতে হয়, কারা আসছে। সেই খাতা থেকে এসবির লোকেরা প্রতিদিনই নাম টুকে নিচ্ছে। ওঁরা এলে অল্প সল্প গল্প হয়, খাওয়া হয় দাওয়া হয়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়, রাত হয়। কিন্তু যা হয় সব ঘরে হয়। বাইরে নয়। বাহির আমার জন্য নয়। খোলা হাওয়া আমার জন্য নয়। মুক্তাঙ্গন আমার জন্য নয়। মৌলবাদিরা জোট বাঁধছে, খবর পাই। মসজিদ মাদ্রাসাগুলোয় ডাক দেওয়া হচ্ছে আন্দোলনের। সভার আয়োজন হচ্ছে। বড় সড় মিছিলের জন্য জল্পনা কল্পনা হচ্ছে। এক বিকেলে বাড়িতে কেউ নেই। ইয়াসমিন মিলন বাইরে, মা ময়মনসিংহে। আমি আর মিনু কেবল আছি। এমন সময় দরজায় শব্দ। দরজায় ছিদ্র দিয়ে দেখি ছ জন টুপিঅলা দাঁড়িয়ে আছে। কি চায় ওরা! মিনুকে বলি, দরজা না খুলে জিজ্ঞেস করতে, কাকে চায়। মিনু চেঁচিয়ে শুধায়, কারে চান?
দরজা খোলেন।
কারে চান কন?
দরজা খোলেন আগে। তারপরে বলি, কারে চাই।
মিনুকে আমি ইঙ্গিতে বলে দিই যেন দরজা না খোলে, যেন বলে দেয় কেউ নেই বাড়িতে। মিনু বলে। কিন্তু চলে যায় না ওরা, থাকে, থেকে দরজায় বিকট শব্দে ওরা লাথি দিতে শুরু করে। কলিং বেল চেপে ধরে রাখে। পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট পার হয়ে যায়, দরজায় লাথি কষা কলিং বেল চেপে রাখা কিছুই থামছে না। আমি কুলকুল করে ঘামছি। ইন্টারকম কাজ করছে না। ফোন ডেড। এই ন তলা থেকে চিৎকার করে কাউকে ডাকলে কেউ শুনবে না। দরজায় যত রকম সিটকিনি আছে কব্জা আছে সব লাগিয়ে মিনুকে নিয়ে আমার লেখার ঘরটিতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকি। ওদিকে সদর দরজাটি ভেঙে ফেলতে চাইছে ওরা। ভেঙে ফেলবে, তারপর যে ঘরে বসে আছি, সে ঘরের দরজাটিও ভেঙে ফেলবে, তারপর! তারপর পাঁচজন আমার হাত পা মাথা চেপে ধরে থাকবে, একজন তার পাঞ্জাবির তল থেকে রামদা বের করে আমার গলাটি কাটবে। আমি দুহাতে গলাটি আড়াল করে রাখি। শরীর শিথিল হতে থাকে। শিথিল হতে হতে নুয়ে পড়তে থাকে, কুঁকড়ে শুয়ে থাকি মেঝেয়ে। মিনু, কালো মিশমিশে হাড়গিলে দাঁতাল মেয়েটি (কাজের মেয়ে + আপন ফুপাতো বোন) আমার মাথার কাছে নিঃশব্দে বসে থাকে। আমরা কেউ কারও শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাই না। প্রচণ্ড ঘুম পেতে থাকে আমার।
ঘুম থেকে উঠে দেখি বাড়ি কলকল করছে। মিলন আর ইয়াসমিন ফিরে এসেছে। মিনু বলল, লোকগুলো আরও অনেকক্ষণ ছিল ওখানে। অনেকক্ষণ কতক্ষণ! আধঘন্টা? একঘন্টা? আমার জানতে ইচ্ছে করে না। মিলনকে পাঠিয়ে দিই দরজার জন্য শক্ত তালা কিনতে। নিচের নিরাপত্তা প্রহরীদের জিজ্ঞেস করি কেন তারা ছটি দাড়িটুপিঅলাকে আমার বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দিল। প্রহরীরা জানিয়ে দেয় ছ জন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে তা বলেনি তাদের কাছে। দু নম্বর দালানের কোনও এক বাড়িতে যাচ্ছে বলেছে। এর মানে যে কেউই আবদুল জলিল বা মান্নান তরফদারের বাড়িতে যাচ্ছে বলে আমার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াতে পারে। ইন্টারকমে তো নিচ থেকে খবর দিতে হয় আগে, কিন্তু যদি ইন্টারকম কাজ না করে, যেমন অকেজো হয়ে যায় মাঝে মধ্যে! প্রহরীদের বলে দিই, আমার বাড়িতে কেউ যদি আসতে চায়, যদি ইন্টারকম কাজ না করে, তবে প্রহরীদের কেউ যেন আগন্তুককে একা আসতে না দিয়ে সঙ্গে আসে। ‘ওপরে যাবে যে, আমাদের তো এত বাড়তি লোক নাই ম্যাডাম।’ নেতাগোছের এক প্রহরী আমাকে জানিয়ে দেয়।
‘এখনও সময় আছে, তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যা, নয়ত ঘোষণা দিয়ে হিন্দু হয়ে যা। এ দুটোর কোনও একটি না হলে বিপদ হবে।’ চিঠির বাক্সে কেউ ফেলে রেখে গেছে কাগজটি। খোলা কাগজের হুমকি তো আছেই, উড়ো চিঠিও আসছে। ‘ধর্মের বিরুদ্ধে যদি আর একটি কথা লিখিস, তবে সেই দিন থেকে তোর বেঁচে থাকা হারাম হয়ে গেল মনে রাখিস।’ ফোনেও অচেনা কর্কশ কণ্ঠ মাথা ফাটাবো, হাত কেটে দেব, পা ভেঙে দেব, রগ কেটে দেব, রাস্তায় ফেলে গণধর্ষণ করব, মুন্ডু কেটে হাতে ধরিয়ে দেব বলে যাচ্ছে। আমি টের পাচ্ছি খুব কাছে কোথাও ওত পেতে আছে আততায়ী। আমার ঘরবন্দী জীবনে সুখের ঝরনা বইছে। বিপন্ন আমি বিমর্ষ হয়ে বিমূঢ় বসে থাকি। বিক্ষুব্ধ বিক্ষিপ্ত মন। কী করি! কায়সার এলে তার মুখে নয়, তার বগলের কালো ব্যাগটির দিকে চোখ যায়। ব্যাগটি থেকে বের করে নিই কালো পিস্তলটি। হাতে নিলেই গা শিরশির করে। ভেতরের বুলেট খুলে রাখে কায়সার, তারপরও শিরশির যায় না। আত্মরক্ষার জন্য যে কোনও একটি অস্ত্র প্রয়োজন আমার, হাড়ে মজ্জায় টের পাই। অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন, তসলিমার ওপর যেরকম বিপদ আসছে, ওর কাছে একটি পিস্তল থাকা উচিত। যখন পড়েছিলাম লেখাটি, মর্ম বুঝিনি, বরং সঙ্গে সঙ্গেই খারিজ করে দিয়েছিলাম উদ্ভুট্টি প্রস্তাবটি। পিস্তলটি আমি রেখেছি কাউকে শখ করে খুন করার জন্য নয়, নিজেকে রক্ষা করার জন্য। খুন করতে যদি কেউ আসে তবে এটি হাতে থাকলে হয়ত নয় আবার হয়ত বা পার পাওয়া যাবে। কিছু কিছু দুঃসময় মানুষের জীবনে আসে, যখন কিছুরই নিশ্চয়তা থাকে না, হয়ত বার ওপরই ভরসা করতে হয়। কিন্তু যেদিন রাখি পিস্তলটি সেদিনই সন্ধার পর এক সাংবাদিক ফোনে খবর দিল যে মতিঝিল থানা থেকে পুলিশ আসছে আমার বাড়িতে তল্লাশি চালাতে। কেন তল্লাশি, কিসের তল্লাশি? মা ছটফট করছেন পাগলের মত। ‘এখন কি করবি? কই সরাইবি আপদটারে?’ মা আলমারির কাপড়ের তল থেকে পিস্তলের ব্যাগটি বের করে জায়গা খুঁজছেন লুকোনোর, বড় তোশকের তলে একবার রাখছেন, আবার দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে হাঁড়িপাতিলের ভেতর রাখছেন। আমি করুণ কণ্ঠে বলি, ‘মা, তল্লাশি চালাইলে যেইখানেই রাখো, সেইখান থেইকাই বাইর করব। লুকাইয়া লাভ নাই।’ মনে মনে বলি, এবার বোধহয় ওরা পেয়েই গেল কোনও ছুতো!
সেসময় বিকেলের হাওয়া খাওয়া মেজাজে ডাক্তার রশীদ হেলে দুলে আসেন বাড়িতে। ঘটনা খুলে বলি, যা করার খুব দ্রুত করতে হবে, এক্ষুনি আপদ সরাতে হবে, পুলিশ আসছে। রশীদের কালো মুখটি হাসির ছটা মিলিয়ে দিয়ে আরও কালো হয়ে গেল। রশীদের ঘাড়ে এই আপদ বিদেয় করার ভারটি আমি কোনও রকম ভাবনা চিন্তা না করেই দিয়ে দিই। আসলে দিতে হয় না, নিজেই তিনি দায়িত্বটি নেন। পিস্তলটি এখন কোথায় লুকোবেন? শার্টের তলে, প্যাণ্টের ভেতর? ভাবার জন্য কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন। কী করে নেবেন তিনি এটি! এক একটি মুহূর্ত এক একটি ঘন্টার মত দীর্ঘ। শেষ পর্যন্ত হাতে নিলেন ব্যাগটি, যেন টাকা পয়সা কাগজ পত্তরের ব্যাগ। লুকোলেই মনে হবে লুকিয়েছেন কিছু, তার চেয়ে এই ভাল। হাতে থাকবে আপদ, কেউ আপদ বলে ভাববে না। আমি যেন পুলিশ দেখলেই দরজা না খুলি, তাদের পরিচয়পত্র যেন দেখতে চাই, হাতে কোনও তল্লাশির আদেশ আছে কী না যেন দেখতে চাই উপদেশটি দিয়ে রশীদ বেরিয়ে গেলেন দ্রুত, মিলনকে সঙ্গে নিলেন। খুব স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে খুব স্বাভাবিক ভাবে মিলনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি মিলনকে নিয়ে রিক্সায় ওঠেন। রিক্সায়, কারণ এসময় গাড়ি নিলে, পথে, আমার গাড়ি বলেই গাড়ি থামাতে পারে পুলিশ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নামেন রিক্সা থেকে। নেমেই দেখেন হাসপাতালের আঙিনায় প্রচুর পুলিশ আর ছাত্র ডাক্তারের জটলা। এখন পিছু হটবেন, নাকি সামনে যাবেন! রশীদ মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিলেন সামনে যাবেন। সামনে হেঁটে যাবার সময়ই এক চেনা ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন, জানালেন ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হয়েছে, একজন ছাত্র গুলি খেয়ে মারা গেছে। রশীদের ঘাম কপাল বেয়ে গাল বেয়ে বুকে নামছে। মিলনের দুরু দুরু বুক, জিভ শুকিয়ে কাঠ। ম্যাড়ম্যাড়ে স্বরেও সে যে কিছু বলবে, সে শক্তিও হারিয়েছে। পাঁচ হাত দূরে পুলিশ। ছাত্র মরার খবর দেওয়া ডাক্তারটি রশীদের হাতের ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হাতে কি আপনার? মাল নাকি?’ ঘর্মাক্ত রশীদ মুখে জোর জবরদস্তি করে ‘আরে কী যে বলঞ্চ জাতীয় হাসি ফুটিয়ে রোগীর পাশে ডাক্তার যেমন করে হাঁটেন তেমন করে হেঁটে গেলেন। সোজা অপারেশন থিয়েটারে। থিয়েটারের ভেতরের আলমারিতে। সে রাতে আমার বাড়িতে পুলিশ আসেনি। না এলেও যে কোনওদিন আসতে পারে। লাইসেন্সহীন পিস্তলের ঝুঁকি আর নিচ্ছি না। যথাবিহীত আশঙ্কাপূর্বক ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে এটির প্রকৃত মালিক কায়সারকে এটি দিয়ে উদ্ধার হই।
শেষ পর্যন্ত আমার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বসানো হয় বাড়ির দরজায়। মতিঝিল থানায় পুলিশ মোতায়েন করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, আমার শিমুল-তুলো অনুরোধ ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিয়েছে থানার লোকেরা। জানিয়ে দিয়েছে মতিঝিল থানা আমাকে নিরাপত্তা দেবে না যতক্ষণ না থানায় তারা আদালতের আদেশ পায়। আদালতের আদেশ পেতে হলে একজন উকিলের প্রয়োজন। মানবাধিকারের জন্য দেশের দুজন বড় ব্যারিস্টার আদালতে লড়ছেন, ডক্টর কামাল হোসেন এবং আমীরুল ইসলাম। ডক্টর কামাল হোসেনের সঙ্গে সরাসরি আমার আলাপ না থাকলেও তাঁর কন্যা সারা হোসেনের সঙ্গে অতি সম্প্রতি আলাপ হয়েছে। তিনি আমার খোঁজ নিয়েছিলেন তাঁর চেনা দুজন বিদেশী মানবাধিকার কর্মী ঢাকায় এসে আমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন বলে। সারা হোসেনই আমাদের কথা বলার ব্যবস্থা করে দেন মতিঝিলে ডক্টর কামাল হোসেনের আপিসে। সারা নিজে ব্যরিস্টার, অক্সফোর্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে এসে তাঁর বিখ্যাত আইনজ্ঞ বাবার সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে সারা। সাদা সাদা সালোয়ার কামিজ পরেন। শরীরে একতিল মেদের চিহ্ন নেই। বাংলায় কথা বলেন, কিন্তু বাংলায় নয়, ইংরেজিতেই যে তিনি কথা বলতে বেশি অভ্যস্ত তা বোঝা যায় যখন তিনি খুব সচেতন ভাবে একটিও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে কথা বলেন। যে শব্দগুলো আমরা সচরাচর ইংরেজিতে বলি, তিনি সেসবের বাংলা বলেন, অপ্রচলিত যদিও। জাজকে বিচারক, হাই কোর্টকে উচ্চ আদলত, লোয়ার কোর্টকে নিম্ন আদালত, জাস্টিসকে ন্যায়-পরতা বলেন। আইনের সমস্ত শব্দের যদি বাংলা করতে হয়, তবে অনেক বাংলা শব্দই আমার বিশ্বাস সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব হবে। সারার অনেক বাংলা শব্দই আমার কানে অদ্ভুত ঠেকে। নিজেকে অনেকটা সেই রিক্সাঅলার মত মনে হয়, রিক্সারোহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাইলে যে বলেছিল যে সে চেনে না বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়, আরোহী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর গন্তব্যে থেমে বলেছিল, ‘আরে ইনিভার্সিটি আইবেন, সেইটা তো কইবেন।’ সারাই ফতোয়ার বিরুদ্ধে একটি মামলা নথিবদ্ধ করেন। অবশ্য এতে কাজ হয় না, কারণ আদালত থেকে বলে দেয়, সিলেটের সাহাবা সৈনিক পরিষদের বিরুদ্ধে মামলা করতে হলে আমাকে সিলেটে যেতে হবে, ঢাকার আদালত এই মামলা নেবে না। মরতে যাবো আমি সিলেটে! শেষ পর্যন্ত সারা হোসেন আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন। আমার অনুপস্থিতিতে আদালত কিছুই করতে রাজি নয়। অগত্যা আমাকে যেতে হল পুরোনো ঢাকায় সারার নিম্ন-আদালতে। ঝুঁকি নিয়েই। সরকারের সামান্যও যদি নীতিবোধের বালাই থাকত, এ সময় সাহাবা সৈনিক পরিষদের বিরুদ্ধে আইন অমান্য করার মামলা ঠুকে দিত। কিন্তু সরকার এ ব্যপারে নীরব, যেন সাহাবা সৈনিক পরিষদ অন্যায় তেমন করেনি। অন্যায় আমিই করেছি, এই ফতোয়া প্রাপ্যই ছিল আমার। আদালতের আঙিনা গিজগিজ করছে লোকে। সকলের চোখ আমার দিকে। কে জানালো এই ভিড়ের লোকদের যে আমি আজ আদালতে যাবো! অদৃশ্য কোনও একটি শক্তি কাজ করছে, আমার চলাচল এই শক্তির নখদর্পণে। ভিড়ের লোকদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয়। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব কাজ সেরে নিতে হয়। আদালতে বিচারকের চেয়ারে বসা ম্যাজিস্ট্রেট গম্ভীর গলায় বললেন, ‘এমন সব কথা লিখলে দেবেই তো ফতোয়া!’ ইচ্ছে তাঁর হয় না তবুও তাঁকে থানায় আদেশ দিতে হয় আমার বাড়িতে পুলিশ পাঠাতে। আদালত থেকে বাড়ি ফিরে পাহারা পুলিশের অপেক্ষা করতে থাকি। পুলিশের কোনও চিহ্ন নেই। অনেকদিন চলে গেল। আদালতের আদেশ পুলিশও যে অমান্য করতে পারে, তা আমার আগে জানা ছিল না, এখন জানা হয়। মতিঝিল থানা থেকে পুলিশ আসে শেষ পর্যন্ত, আসে অক্টোবরের ১৪ তারিখে। আগের দিন আমাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে লেখা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের একটি কড়া চিঠি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে বলেই কী! কেবল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নয়, প্রায় সব আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা আমার নিরাপত্তার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করছে। এদিকে ফতোয়ার বিরুদ্ধে দেশের ছত্রিশজন লেখক বুদ্ধিজীবী ফতোয়ার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন। ফতোয়ার পক্ষে বিপক্ষে লেখালেখি চলছে। কৃশকায় দুটো পুলিশ আমার বাড়ির দরজার সামনে বসে বসে ঝিমোয়। ঝিমোয়, তবু বাড়ির সকলে স্বস্তির শ্বাস ফেলে। মা ঝিমোনো পুলিশদের চা বানিয়ে খাওয়ান। বলেন, ‘পুলিশগুলার জন্য মায়া হয়।’ বারান্দায় দুটো চেয়ার পাঠিয়ে দেন ওদের বসার জন্য। এপির ফটোগ্রাফার নাদুস নুদুস পাভেল এসে দাঁড়ানো পুলিশের ছবি তুলে নিয়ে গেল, মজার জিনিস সম্ভবত। আমার কাছে অবশ্য এসবকে মজা বলে মনে হয় না। বরং অস্বস্তি লাগে পুলিশের অমন বসে থাকা দেখে। পড়শিরা বলাবলি করছে পুলিশের উপস্থিতি তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে, যে কোনও সময় না আবার বাড়ি আক্রমণ হয়। ইয়াসমিন এক ক্রুদ্ধ বাসিন্দাকে বলে এল, পুলিশ থাকলে তো বরং নিরাপদ বোধ করার কথা! কিন্তু নিরাপদ কেউ বোধ করে না। দরজার বাইরে পা রাখলেই লক্ষ করি আমার দিকে চেয়ে আছে অনেকগুলো পলক না পড়া চোখ। বাড়িতে নিরাপত্তা, বাড়ির বাইরে টিকটিকি। যেখানেই যাই না কেন, টিকটিকি পিছু নেয়, কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি তা সরকারি খাতায় লেখা হয়ে যায়।
উদ্ভট কিছু হতে চলেছে দেশে। টের পাই। গন্ধ পাই। মৌলবাদী নেতারা, যাদের ক্ষমতা অনেক, সব একজোট হচ্ছেন। বড় রাস্তায়, ছোট রাস্তায়, অলিতে গলিতে মৌলবাদীদের সভা হচ্ছে, বিষয় তসলিমা। নেতারা সাংবাদিক সম্মেলন করছেন, বিষয় তসলিমা। মাঠে ময়দানে সভা। তসলিমার জন্য একটি কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা। নেতারা দেশের সর্বস্তরের মানুষকে আহবান করছেন তাঁদের ডাকে সাড়া দিতে। মসজিদে মসজিদে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে তসলিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার। শত সহস্র মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রস্তুত মাঠে নামার জন্য। ঢাল প্রস্তুত। তলোয়ার প্রস্তুত। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়ছে। যেন তসলিমাকে এক্ষুনি একটি শাস্তি না দিলে ইসলামের সর্বনাশ হবে, দেশ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মিলন মাঝে মাঝে জুম্মাহর নামাজ পরতে শান্তিনগর মসজিদে যায়। মসজিদে বিলি করা লিফলেট হাতে বাড়ি ফেরে। কেবল মসজিদেই নয়, রাস্তাঘাটে বিলি হচ্ছে হরেক রকম তসলিমা বিরোধী লিফলেট। একদিন আমার হাতে মিছিলের একটি লিফলেট দিল মিলন। মিছিল হবে। বিশাল মিছিল।
নারায়ে তাকবীর = আল্লাহু আকবার
দ্বীন ইসলামের অবমাননা = মুসলমান সইবে না
রাসুলুল্লাহর অবমাননা = চলবেনা চলবেনা
বি.জে.পির তাবেদার = তসলিমা হুশিয়ার
রুশদীর সহযোগী = তসলিমা সাবধান
কুখ্যাত তসলিমার = বিচার চাই করতে হবে
নাস্তিক, মুর্তাদ বেঈমান = হুশিয়ার সাবধান
পবিত্র কোরআন, দ্বীন ইসলাম এবং মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে জঘন্য কটাক্ষকারী, দেশের অব্যাহত সম্প্রীতি ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, কুখ্যাত মুর্তাদ খোদাদ্রোহী, রাসুলের দুশমন, শয়তান রুশদীর দোসর ভারতের উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বি,জে,পির দাবার গুটি, নারী সমাজের কুলাঙ্গার
মুর্তাদ নিলর্জ্জ তসলিমা নাসরিনের
০গ্রেফতার ০ কঠোর শাস্তি ০ এবং সব আপত্তিকর লিখনী বাজেয়াপ্তের দাবীতে
বিরাট জনসভা
স্থানঃ বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেইট
আরিখঃ ১৮ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ৯৩
সময়ঃ বেলা ২ ঘটিকা
ঈমানী চেতনা এবং দেশ, জাতি ও নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মিছিল সহকারে দলে দলে যোগদান করুন।
আবেদনে ঃ
সর্বস্তরের ওলামা ও মাশায়েখগণের পক্ষে
(শাইখুল হাদীস মাওলানা ) আজিজুল হক
(মাওলানা গাজী ) ইসহাক
শায়খুল হাদীস, পটিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম
(মাওলানা মুফতী) আব্দুর রহমান
মহাপরিচালক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার,ঢাকা
(মাওলানা) মুহিউদ্দিন খান
সম্পাদক মাসিক মদীনা, ঢাকা
(মাওলানা কবি) রুহুল আমীন খান
(মাওলানা) আব্দুল গাফফার
মুফাসসিরে কোরআন, ঢাকা
(মাওলানা মুফতী) ওয়াহিদুজ্জামন
মোহাদ্দিস, বড়কাটরা মাদ্রাসা, ঢাকা
(মাওলানা) আব্দুল জব্বার,
মহাসচিব, বেফাকুল মাদারিস, বাংলাদেশ
(মাওলানা) নূর হোসাইন কাসেমী,
মুহতামিম, বারিধারা মাদ্রাসা, ঢাকা
(মাওলানা ক্বারী) ওবায়দুল্লাহ
খতিব, চকবাজার শাহী মসজিদ
(মাওলানা) মুহম্মদ হাবীবুর রহমান
আহবায়ক, বাংলাদেশ ছাহাবা সৈনিক পরিষদ
মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী দাঁড়ালেন, মুস্তফা নূরুউল ইসলাম লিখেছেন, ‘কী এক উদ্ভট দেশে, অতি বৈরী পরিবেশে বসবাস আমাদের, যেখানে কাউকে তার আপন স্বাধীনতায় ভাবতে দেয়া হবে না, স্বপ্ন দেখতে দেয়া হবে না। ধিককার দিই নিজেদেরকেই, এই পাপকাণ্ড অবলীলায় এখন ঘটে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধসম্ভূত আমাদের বাংলাদেশে। নইলে তসলিমা নাসরিন লেখেন, লিখে তাঁর ভাবনার কথা বলেন – কারা সেই বিকল্প হাকিম তাঁর বিরুদ্ধে চরম দণ্ড প্রদানের ফতোয়া জারি করার ধৃষ্ট সাহস যাদের? তসলিমার অপরাধ, তিনি অন্ধকারে, কুসংস্কারের জড়বুদ্ধির পাহাড়কে আঘাত করেছেন। মতলববাজদেরকে আঘাত করেছেন। তাঁর অপরাধ, তিনি নিজের মত করে লেখেন এবং তাঁর বিশ্বাসজাত উপলব্ধিসমূহ সৎমানুষের আন্তরিকতায় খোলামেলা করে বলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমরা একমত নাও হতে পারি। তাই বলে বিংশ শতকের শেষ দশকে পৌঁছে, একটি স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক সিভিল সমাজে বাস করে লেখকের অধিকারকে নিহত হতে দেব, এটা হতে পারে না।
মনে পড়ছে, নজরুলকে একদা কাফের বলা হয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে শূলদণ্ডের ফরমান জারি হয়েছিল। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা আবুল হুসেন আর কাজী আবদুল ওদুদকে দিয়ে একরারনামা সই করিয়ে নেয়া হয়েছিল। আশঙ্কা হয়, তবে কি সেই মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার পূনরুত্থান ঘটছে?
কিন্তু শেষ সত্যটা এই যে, ইতিহাসের চাকা কদাপি পেছনের দিকে ঘোরে না। আমরা তসলিমা নাসরিনের আপন মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে।’
অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বক্তব্য, ‘তসলিমাকে নিয়ে যা হচ্ছে, বিষয়টি এখন আর সাহিত্যিক নয়, রাজনৈতিক। এখানে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না, আলোচনা হচ্ছে মৌলবাদীদের আক্রমণের বিষয় হিসেবে। মৌলবাদীদের দিক থেকে বিষয়টি রাজনৈতিক। বইয়ের ব্যপারে আগ্রহ তাদের নেই। অথচ তারা এ ধরনের বিষয়ের জন্যই ওৎ পেতে থাকে। পাল্টা বক্তব্য দিয়ে খণ্ডন করে না। এ ক্ষেত্রেও এটা ঘটেছে। এটা রাজনৈতিক। যখনই এ মৌলবাদী দলগুলো সুযোগ পায়, তখনই তারা এসব বিষয় নিজেদের দিকে টেনে নেয়। বক্তব্য যে জায়গায় আছে, সেটাকে তুলে নিয়ে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করে। নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সবারই থাকা উচিত। এসব নিয়ে যারা আক্রমণ করছে তারা প্রগতির শত্রু।’ বদরুদ্দীন উমর, বামপন্থী তাত্ত্বিক আমার অধিকাংশ লেখার সঙ্গে একমত নন, তিনিও বললেন যে আমাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলকাও সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে, তিনি তাঁর ঘোর বিরোধী। ধর্মীয় বর্বরতা প্রতিহত করা দেশের সকল প্রগতিশীল শক্তিরই একটি জরুরী কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন। কে এম সোবহান লিখেছেন, ‘প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার তার মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার। নাগরিক নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব এবং নাগরিকের বিনা বাধায় চলাফেরা করার স্বাধীনতা আছে। নাগরিকের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার দেয়া আছে এই ভষায়, বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না যাতে কোনও ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। যে ভাষায় তসলিমা নাসরিনের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর মৌলবাদী ও রক্ষণশীলরা আক্রমণ করেছে তাতে তার সুনাম নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ন হয়েছে। সরকারের দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতাই আইন শৃঙ্খলার অবনতির অন্যতম কারণ। যারা তসলিমার মেধাকে সহ্য করতে পারে না, তিনি এই বয়সে সাহিত্য জগতে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, সে সম্পর্কে যারা ঈর্ষান্বিত তারাই তার বিরুদ্ধে অশালীন অপপ্রচার চালান। অপব্যাখ্যা দেন তাঁর মতামতের। সে মতামত সম্পর্কে যে অপব্যাখ্যাকারীরা সম্যকভাবে পরিচিত তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তসলিমার প্রতিভার, তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি যাদের কাছে অসহনীয় তারাই তাঁকে হুমকি দেয়, দুর্নাম রটায়।’
ভোরের কাগজে সম্পাদকীয় লেখা হল। ঞ্ছসময় এগিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এগুচ্ছে না বাংলাদেশের সমাজ। এই সমাজকে সব সময়ই পিছনে টানছে সাম্প্রদায়িক বিভেদ, মৌলবাদ, প্রতিক্রিয়াশীলতা। একাত্তরে এই মৌলবাদী শক্তি মুক্তিযোদ্ধাদের অভিহিত করেছিল কাফের বলে। এখানো তারা চালিয়ে যাচ্ছে ধর্মের অপব্যবহার, পবিত্র ধর্মকে ব্যবহার করে যাচ্ছে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে, একের পর এক বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল কর্মী হচ্ছে এদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। এদের সাম্প্রতিকতম টার্ণেট তসলিমা নাসরিন। তসলিমা নাসরিনের লেখা এই ফতোয়াবাজদের উষ্মার কারণ। যে কোনও বই কারও কাছে আপত্তিকর মনে হতে পারে, এক লেখা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, এমন কোনও কথা নেই। তসলিমা নাসরিনের লেখা নিয়েও আছে বিতর্ক, তার লেখার পক্ষে ও বিপক্ষে আছে নানা জোরালো মত। এসব লেখার প্রতিপাদ্য নিয়ে যে কেউ আপত্তি তুলতে পারেন, তবে আপত্তিটা আসা চাই গণতান্ত্রিক উপায়ে, সভ্য পন্থায়। কিন্তু সিলেটের তথাকথিত ছাহাবা সৈনিক পরিষদ দেশের প্রচলিত আইন ও সভ্য রীতির চরম অবমাননা ঘটিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় তসলিমা নাসরিনকে হত্যার আহবান জানিয়েছে। হত্যাকারীকে নগদ ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার দেবার ঘোষণাও দিয়েছে তারা। সিলেটে তারা তাদের কার্যক্রমের সমর্থনে হরতালও আহবানও করেছিল একদিন। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় একখণ্ড মধ্যযুগ। দেশে আইনানুগ সরকার, বিচার ব্যবস্থা, আইনের শাসন প্রচলিত থাকা অবস্থায় কি করে একদল মানুষ একজন লেখককে হত্যার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করতে পারে, তা বোঝা কঠিন।
এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে লণ্ডনভিত্তিক আ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। আইনের আশ্রয় চেয়েছেন তসলিমা নাসরিন। আদালত তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশকে। কিন্তু ওই ধর্মব্যবসায়ীরা বন্ধ করেনি তাদের কার্যক্রম। বরং তারা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে, তারা নেমেছে আটঘাট বেঁধে। দেশের প্রচলিত আইনের ঘোরতর অবমাননা করে যারা দেশটিকে ঠেলে দিতে চায় নৈরাজ্যের দিকে, তারা কি করে এমন প্রকাশ্যে বিনাবাধায় চালিয়ে যেতে পারে তাদের কার্যক্রম? আমরা প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তেমনি লেখকের লেখার স্বাধীনতাও হওয়া উচিত আমাদের অঙ্গীকার। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র বলতে তাই বোঝায়। আমাদের সংবিধান বাক ব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়।”
আজকাল ব্যালেন্স বলে একটি শব্দ খুব চলে পত্রিকা পাড়ায়। বিশেষ করে প্রগতিশীলদের পত্রিকায়। এই সম্পাদাকীয়টির লেজে খানিকটা ব্যালেন্স রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে এভাবে, ঞ্ছকোনও লেখককে হত্যার উস্কানি দেওয়া তাই কিছুতেই সুস্থতার লক্ষণ নয়। ইসলামের মূল নীতিও তাতে লঙ্ঘিত হয়। (হয় কি? ইসলাম কিন্তু বলে হয় না)পাশাপশি লেখকের স্বাধীনতা বলতে যে কেবল যা খুশি লেখার স্বাধীনতা বোঝায় না ( কার খুশি মত লিখতে হবে লেখককে?), তার সঙ্গে আপনা আপনিই যুক্ত হয় এক ধরনের দায়িত্ব ( আমি কি দায়িত্বহীনতার কাজ করেছি?), তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না কোনও প্রকৃত লেখককে ( আমি তবে প্রকৃত লেখক নই)। কোনও সচেতন লেখক (আমি তবে নিশ্চিতই অসচেতন লেখক) নিশ্চয়ই চাইবেন না, তার লেখা ব্যবহৃত হোক মতলববাজদের রাজনৈতিক স্বার্থে (লেখক যখন লেখেন, তখন কি করে জানবেন তাঁর লেখা মতলাববাজরা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করবে কি না)।”
নিঃসন্দেহে ভাল লেখা। ভাল লেখার আকালে এটিই ভাল লেখা। আকাল বলছি এই জন্য যে, ফতোয়ার পক্ষেই অধিক লেখা ছাপা হচ্ছে। ফতোয়ার বিপক্ষে কোনও যুক্তিবাদীর কলম হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে ওঠে। শামসুর রাহমান দুঃখ করে লেখেন, ঞ্ছবাংলাদেশে বসবাস করব, অথচ প্রায়শই মন খারাপ হবে না, এরকম কথা বলা মুশকিল। মন খারাপ করার মত ঘটনা এখানে হরহামেশা ঘটছে। খবরের কাগজ পড়তে শুরু করলেই মন খারাপ হয়ে যায়। হবেই বা না কেন? সড়ক দুর্ঘটনা, হরতাল পালনকারীদের উপর পুলিশী জুলুম, শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস, লেখকের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ, ফতোয়াবাজদের দৌরাত্মে গ্রামাঞ্চলে নারী নির্যাতন, কোনও কোনও নারীর প্রাণনাশ, চুরি ডাকাতির হিড়িক, মৌলবাদীদের তর্জন গর্জন, মুক্তমতি মানুষের বিড়ম্বনা, এইসব কিছুই যুক্তিবাদী খোলা মনের ব্যক্তিদের ব্যথিত করে, বিষণ্ন করে, কখনো কখনো ক্ষুব্ধ করে। এই ক্ষোভ প্রকাশ করাও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা মুখ খোলেন, তাঁরাই পড়েন বিপদে। অশিক্ষা যেখানে মুকুট পরে বেড়ায়, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার এবং গোঁড়ামি যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে যুক্তিবাদী মানুষের কল্কে তো জোটেই না, বরং তাঁরা হয়ে পড়েন পশ্চাৎপদ, কূপমণ্ডুকদের আক্রমণের লক্ষ্য। আরো খারাপ লাগে, যখন দেখি একজন মুক্তমতি লেখক প্রতিক্রিয়াশীলদের, মৌলবাদীদের টার্ণেট হন তখন অধিকাংশ লেখক থাকেন উদাসীন, সেই লেখকের পক্ষে দাঁড়াবার কোনও প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, যেন এটা কোনও ইস্যু নয়। মৌলবাদীদের আক্রোশের ঝড়ে বিপণ্ন লেখকের পক্ষ অবলম্বন করা দূরে থাক, কখনও কখনও তাঁর বিরুদ্ধে বাক্যাবলী খরচ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁরাও আক্রমণ করেন সেই লেখককে। আক্রান্ত লেখকের সব মতের সঙ্গে সবাই একমত হবেন, এটা আশা করা যায় না। কিন্তু মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও একজন লেখকের স্বাধীনতার সপক্ষে লেখককুল কলম না ধরলে কারা ধরবে?”
শামসুর রাহমানের এই আহবানে যে লেখককূল কলম হাতে বসে গেলেন তা নয়। কেউ কেউ বলছেন, আমি ধর্ম নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করি, আমার পক্ষে দাঁড়াবার কোনও মানে হয় না, কেউ বলছেন, ইচ্ছে করেই ধর্মের সমালোচনা করে আমি মৌলবাদীদের ক্ষেপিয়ে তুলেছি, তাদের হাতে ইস্যু ছিল না, ইস্যু দিয়েছি, তাদের শক্তি ছিল না, শক্তি দিয়েছি, আমার কারণেই দেশে মৌলবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, নিজেকে বিতর্কিত করে তোলার জন্য আমি এসব করেছি, কেউ বলছেন, নারী স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে আমি সীমা ছাড়িয়ে যাই, আমার পক্ষে মন্তব্য করা তাঁদের উচিত নয়। তারপরও কেউ কেউ কিছু লিখছেন। ওদিকে বিপক্ষে একশটি লেখা ছাপা হচ্ছে, এদিকে পক্ষে একটি। মৌলবাদিরা আঁটঘাট বেঁধে লেগেছে। জেহাদ ঘোষণা করেছে। ক্ষমতাসীনদের সহায়তা পেলে জেহাদে বিস্তর সুবিধে। সুবিধে পেয়ে পেয়েই এগোচ্ছে তারা। তাদের যত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকা আছে, নিজেদের মধ্যে মতের মিল না থাকলেও তারা আমার বিরুদ্ধে প্রতিদিন লিখে যাচ্ছে। মিথ্যে কথা। বানানো কথা। অসভ্য অশ্লীল কথা। উদ্দেশ্য পাঠকের মনে যেন ঘৃণা জন্মায়, যেন এই ঘৃণা গায়ে গতরে বড় হতে থাকে এবং বড় হতে হতে এমন অবস্থায় পৌঁছোয়, যে, পাঠক বলতে বাধ্য হয় যে আমার জন্য একটি মৃত্যুদণ্ড অতীব জরুরি। মৌলবাদী নয়, এমন পাঠকও যেন সেসব মিথ্যে পড়ে আঁতকে ওঠে এবং আমার ফাঁসির দাবি তোলে। অথচ সেই তুলনায় প্রগতিশীল পত্রিকাগুলো, যেসব পত্রিকায় মৌলবাদের বিপক্ষে সচরাচর লেখা হয়, সরব নয়। যেন আমার বিরুদ্ধে মৌলবাদিদের আন্দোলন একটি বিচ্ছিত ঘটনা, যেন এটি আমার ব্যক্তিগত ব্যপার। এখানে তাদের নাক গলানোর কিছু নেই। বড় রাস্তা বন্ধ করে সভা হচ্ছে মৌলবাদিদের, হাজার হাজার মৌলাবাদী মিছিল করছে, রাস্তায় ট্রাফিক থেমে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা, এ তসলিমার ব্যক্তিগত ব্যপার। মৌলবাদিরা তো আমাদের ঘাড়ে কোপ বসাতে আসছে না, আমরা কেন লাফাবো তসলিমার পক্ষে! কিন্তু খুব বড় লেখক যখন প্রতিবাদ করে লেখেন, তখন সেসব লেখা ছাপতে হয় পত্রিকায়, বড় লেখক বলেই ছাপতে হয়, তসলিমার পক্ষে বলে নয়। তবু হঠাৎ হঠাৎ কোথাও কোথাও কোনও বিবেক চেঁচিয়ে ওঠে, দৈনিক সংবাদে শাকিনা হাসীন অনেকটা যাত্রার বিবেকের মত মঞ্চে ঢুকে চিৎকার করে বললেন যে ‘না এটি তসলিমার ব্যক্তিগত ব্যপার নয়, কারণ সারাদেশের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি (চিহ্নিত ও ছদ্ম)- ব্যক্তি, দল ও পত্রপত্রিকা জেহাদে অংশ নিচ্ছে, সুতরাং সকল ক্ষুদ্র স্বার্থ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সংকীর্ণতা ও পরশ্রীকাতরতার উর্ধে উঠে এই হামলাকে যেন প্রগতিশীল লেখকরা নিজেদের ওপর আঘাত হিসেবে বিবেচনা করেন। প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি গা বাঁচানোর নীতি অনুসরণ করে চলতে চলতে ভোটের বাক্সের দিকে তাকিয়ে এই যে অন্ধত্বের অভিনয় করে চলেছেন, কিন্তৃ যতই অন্ধ আর বোকা তারা সাজুন না কেন প্রলয়ের তাণ্ডব তাঁরাও যে এড়াতে পারবেন না, তা এখনই বুঝতে হবে।’ এখন যদি না বোঝেন, তবে, শাকিনার আশঙ্কা, অনেক দেরী হয়ে যাবে। না এ বুঝতে কোনও রাজনৈতিক দলের কেউ চাইলেন না। ব্যপারটি অনেকটা আমার ব্যক্তিগতই থেকে গেল। সাধারণত মৌলবাদিদের যে কোনও উত্থানে আওয়ামি লীগ পথে নামে। এখন আওয়ামি লীগ মৌনব্রত পালন করছে। আরে বাবা! আমার পক্ষে কথা না বল, অন্তত ফতোয়ার বিপক্ষে কথা বল। সে কথা বলতেও যদি তসলিমা নামটি উচ্চারণ করতে হয়, তাই করা হচ্ছে না। তসলিমা নামের সঙ্গে নাস্তিকতা জড়িয়ে আছে, এই নামটি উচ্চারণ করলে আওয়ামী লীগের ধর্মের লেবাস যদি খুলে যায়, তাই ভয়। কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড ফরহাদ মারা যাওয়ার পর মহাসমারোহে তাঁর জানাজা পালন হয়েছে, কোরান খতম কুলখানি কিছুরই অভাব ছিল না। বাম দলের সদস্যরা নাস্তিক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন সে দীর্ঘদিন। সুতরাং তাঁদের দলের সঙ্গে আমার নামটি যোগ করলে যদি আবার ধর্মহীনতার কালি লাগে তাঁদের গায়েও! তবে তো যুগ পার হয়ে যাবে ওই কালি দূর করতে। সুতরাং কোন নাস্তিককে ফতোয়া দেওয়া হলে সে ফতোয়া নাস্তিক সামলাবে। আমাদের পূর্বনেতারা যেমনই ছিলেন, আমাদের দলকে ধরে বেঁধে আমরা অনেক আগেই আমরা মুসলমানি করিয়েছি, আল্লাহ রসুল মেনে চলি, আমাদের দিকে নজর দিও না। বাকি যে দল আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাসদ, সত্তর দশকে শেখ মুজিবর রহমানের বিরোধিতা করার জন্যই যে দলের জন্ম হয়েছিল। শেষ মুজিবের মৃত্যুর পর দলটির বেঁচে থাকার কোনও অর্থ না থাকলেও বেঁচে আছে, এরকম বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না বলে দলের অনেক নেতাই এ দলে ও দলে এমনকী আওয়ামি লীগেও গিয়ে ভিড়েছেন। নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের আট দলীয় জোটে জাসদ, জাসদ ভেঙে বেরিয়ে আসা বাসদও ছিল। বাকি যে দল আছে এর মধ্যে বড় হল জাতীয়তাবাদী দল, সংক্ষেপে বিএনপি। জাতীয়তাবাদী দলে আর মৌলবাদী দলে কোনও ফারাক নেই বললে চলে। বিশেষ করে একানব্বইএর নির্বাচনে জামাতের সাহায্য সহযোগিতায় করুণা কৃপায় বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর অল্প যেটুক ফারাক ছিল, সেটিও প্রায় যাচ্ছে যাবে করছে। সংসদে এখন জামাতে ইসলামির আঠারোটি আসন। চল্লিশ লক্ষেরও বেশি ভোট পেয়েছে জামাতে ইসলামি। আমাদের কবি-এরশাদ এখন জেলের ভাত খাচ্ছেন, ছাড়া পেলে তিনিও যে দলবল সহ ভিড়তেন মৌলবাদীর দলে, এ নিশ্চিত। জাতীয় পার্টির কোনও চরিত্র ছিল না, এরশাদের জেল হয়ে যাওয়ার পর পরই জাতীয় পার্টির বড় বড় নেতা আওয়ামি লীগে আর বিএনপিতে ভিড়ে গিয়েই তা প্রমাণ করেছে। দল বদল এ দেশের রাজনীতিতে ডাল ভাতের মত ব্যপার। ধূর, আজ এ দলে সুবিধে হচ্ছে না, ও দলে চলে যাই, ও দলে সুবিধে না হলে আরেক দলে চলে যাবো। নীতি আদর্শের বালাই না থাকলে এই হয়। মৌলবাদীরা তাঁদের নীতি আর আদর্শে অটল, জামাতে ইসলামির কাউকে দেখা যায় না অন্য দলে নাম লেখাতে। আওয়ামি লীগ সবসময় ফাঁক ফোকর খোঁজে ক্ষমতাসীন বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যখন গণআদালত বসিয়ে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করছিল, আওয়ামি লীগ উড়ে এসে জুড়ে বসে জনপ্রিয়তা পেতে নির্মূল কমিটির দোসর হয়ে গেল, অথচ লেখকের বিরুদ্ধে জামাতপন্থী মৌলবাদিদের ফতোয়া দেওয়ার অন্যায়টি যখন সরকার দেখেও দেখছে না, দেশব্যাপী মৌলবাদিরা আগ্নেয়গিরির লাভার মত বেরিয়ে আসছে দেখার পরও মুখে যখন কুলুপ এঁটে বসে আছে বিএনপি সরকার, এই আওয়ামি লীগই তখন আশ্চর্য রকম ভাবে নিশ্চুপ। সরকার বিরোধী একটি চরম আন্দোলন শুরু করার জন্য এ ছিল একটি মস্ত বড় সুযোগ কিন্তু এই চমৎকার সুযোগটির দিকে সুযোগ সন্ধানী আওয়ামি লীগ মোটেও হাত বাড়াচ্ছে না। কারণ একটিই। তসলিমা। এদিকে সারাদেশের আলেমরা বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তাদের মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুতি প্রয় চূড়ান্ত। কোনও আলেম ওলামা ইমাম মাওলানা পীর মাশায়েখ কোথাও আর বসে নেই। মুসলিম ঐক্য ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে। ধর্ম ও দেশ বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটিও হয়েছে। ধর্মীয় রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক সব দল একত্র হয়ে ইসলামী ঐক্যজোট বানিয়েছে। আর কী চাই! নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য অন্তত এই ইস্যুতে নেই। পাঁচ দশ হাজার লোকের মিছিল হচ্ছে ঢাকা শহরে। রাজপথ দখল করে আছে মৌলবাদিরা। তারপরও যখন কোনও রাজনৈতিক দল মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে না, কোনও দলই, কোনও মানবাধিকার সংগঠন, কোনও লেখক সংগঠন, কোনও নারী সংগঠন পথে নামছে না তখন আমার ক্ষুদে বন্ধু নাহিদ ঝুনু মিতুল, নিপা তসলিমা সপক্ষ গোষ্ঠী নাম দিয়ে একটি গোষ্ঠী দাঁড় করিয়ে মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান লেখা একটি ব্যনার হাতে নিয়ে নেমে পড়ে মৌন মিছিলে। মিছিল টিএসসি থেকে প্রেসক্লাব পর্যন্ত যায়। তসলিমা সপক্ষ গোষ্ঠী একটি লিফলেটও ছেপেছে। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার পক্ষে প্রগতিশীল বিবেকবান সকল সচেতন মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছে, ‘আসুন দলমত নির্বিশেষে আমরা তসলিমা নাসরিনের পাশে দাঁড়াই। তাঁর পক্ষে সংগঠিত হয়ে সরকারের কাছে দাবি জানাই, তসলিমা নাসরিনসহ নারী ও মানবতার মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে যারা আওয়াজ তুলছে তাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তাসহ তসলিমা নাসরিনের পূর্ণ নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হোক এবং মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।’
সব মিলিয়ে কতজন ছিল সেই মৌন মিছিলে! একশ দেড়শ! বেশির ভাগই মেয়ে। গার্মেণ্টেসএর মেয়েরাও যোগ দিয়েছে। ঝুনু বক্তুতা করতে ভাল জানে, প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে লোক জমিয়ে ফেলে। ঝুনুর সাহস আছে বটে। শার্ট প্যাণ্ট জুতো পরে। ছোট চুল। মেয়ে হয়ে ছেলের পোশাক পরেছে বলে ঝুনুকে অনেক কটুকথা শুনতে হয় রাস্তাঘাটে। ও পরোয়া করে না। মৌন মিছিলের আকর্ষণীয় দিক ছিল, যা শুনেছি, শামীম সিকদার, বিখ্যাত ভাস্কর, টিএসসিএ মোড়ে মিছিলটি দেখে এগিয়ে আসেন এবং নিজে তিনি ব্যানার বহন করেন। বাংলাদেশে শামীম সিকদারের মত সাহসী কোনও মেয়ে আমার জানামতে নেই। আর্ট কলেজের অধ্যাপিকা তিনি। একসময় ওই কলেজের অধ্যাপকগণ শামীম সিকদারের অপসারণের দাবীতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছিলেন। শামীম সিকদার কিন্তু হতাশ হয়ে কেঁদে কেটে আকুল হয়ে পিছু হটেননি। তিনি লড়াই করেছেন এবং সে লড়াইয়ে জিতেছেন। আন্দোলনকারী অধ্যাপকদের সামনে তিনি সশব্দে সদর্পে হেঁটে যান। শামীম সিকদারের বিশাল বিশাল ভাস্কর্য ঢাকা শহরের অনেক জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যেমন দাঁড়িয়ে আছেন শামীম শিকদার নিজের অবস্থানে। আত্মসম্মানবোধ তাঁর প্রবল। নিজের মর্যাদা এতটুকু ক্ষূণ্ন হতে তিনি দেন না। যেমন দেননি সেই ছোটবেলায়, যখন সাইকেল চালিয়ে ইশকুলে যাচ্ছিলেন, আর তার পরনের ওড়না টেনে নিয়ে গিয়েছিল এক ছেলে, সেই ছেলেকে ধরে তো পিটিয়েছেনই, আর কোনওদিন ওড়না পরেননি, কামিজ পাজামাও পরেননি, শাড়ি তো জীবনেও পরে দেখেননি। পরেন শার্ট প্যাণ্ট। পায়ে শক্ত জুতো। হাতে প্রয়োজন হলে রিভলভার রাখেন। সেই কিশোরী বয়স থেকেই শামীম সিকদারের কথা যত শুনেছি, শ্রদ্ধায় আমার তত মাথা নত হয়েছে। শামীম সিকদারের মত হতে ইচ্ছে করত আমার, কিন্তু পারিনি। লজ্জা, ভয় আমাকে গ্রাস করে ছিল সবসময়ই। সেই শামীম সিকদার, নির্মলেন্দু গুণ এবং গুণের কিছু সাঙ্গ পাঙ্গ মৌন মিছিল শেষ করে সাকুরায় গেলেন। ওখানে গিয়ে আমাকে ফোনে খবর দিলেন, যেন যাই। শামীম সিকদারের সঙ্গে কখনও আমার সুযোগ হয়নি ঘনিষ্ঠ বসে কথা বলার। তাঁকে দূর থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখেছি যখন তিনি হাতে হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে টিএসসির সড়কদ্বীপে স্বোপার্জিত স্বাধীনতা নামের বিশাল ভাস্কর্যের কাজ করছিলেন। শামীম সিকদারের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ আমাকে ঠেলে নেয় সাকুরার দিকে। আমি যাচ্ছি, এমন সময় দেখি ছোটদা আমার বাড়ির দিকে আসছেন, তাঁকে তুলে নিই গাড়িতে। সাকুরার পেছনের একটি টেবিল দখল করে বসেছে সবাই। শামীম সিকদারের পরনে শার্ট প্যান্ট, কোমরে শক্ত চামড়ার বেল্ট। পায়ে বুট। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, ‘তোমার পক্ষে তো মিছিল করে আসলাম। খুব ভাল হইছে মিছিল।’ এরপর বিস্তারিত বিবরণ শুনতে হল মিছিলের। শামীম সিকদারের সাহচর্য পেয়ে আমি এমনই উত্তেজিত যে মিছিল তখন আমার কাছে কোনও বিষয় নয়। শামীম আমার কাঁধ চাপড়ে বললেন, ‘ভয় পাবা না। ভয় পাবা না। মোল্লা হারামজাদাগুলা কিμছু করতে পারবে না। অত সোজা নাকি? তুমি ভয় পাইলেই ওরা মাথায় উঠবে। যা লিখতাছ লেইখা যাও। আমরা আছি। কোনও অসুবিধা হইলে আমারে খবর দিবা। দেখি তোমারে কোন শালায় কি করে! পিটাইয়া হাড্ডিগুড্ডি ভাইঙ্গা দিব।’
শামীম তাঁর সিগারেটের প্যাকেট ঠেলে দিলেন আমার দিকে। মেয়েদের সিগারেট খাওয়া যে সমাজে কোনও মানুষ কল্পনাও করতে পারেন না, সেই সমাজে বাস করেই তিনি রাস্তা ঘাটে রেস্তোরাঁ বারে সবখানেই সিগারেট খান। এই একটি মানুষ, কোনওদিন পরোয়া করেননি লোকে কি বলবে তার। আমাকে মদও দেওয়া হয়। মদ খেয়ে অভ্যেস নেই আমার। দুতিন চুমুক খেয়েই দৌড়োতে হয় বমি করতে। বমির কথা চেপে রাখি। আবার না শামীম সিকদার বলে বসেন, ‘আরে মেয়ে, তুমি ওই সামান্য মদও খাইতে পারো না! এর মধ্যেই তিনি বলে বসেছেন, আমি ত ভাবছিলাম তুমি খুব শক্ত মেয়ে, কিন্তু না। তুমি একেবারে হাউজওয়াইফদের মত লজ্জাশীলা। আমি বুঝে পাচ্ছি না, তোমার মত নরম নিরীহ মেয়ের পিছনে মোল্লারা লাগল কেন!’
শাড়ি প্রসঙ্গেও বলেছেন, ‘শাড়ি পরো কেন? শাড়ি একটা পোশাক হইল? শাড়ি পইরা তুমি কি ফাইট করতে পারবা টুপিঅলাদের সাথে? শাড়ি ধইরা কেউ টান দিলেই তো শাড়ি খুইলা পড়ে। শাড়ি ছাড়তে হবে।’
আমি যখন মোল্লাদের মিছিল হবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে শামীম সিকদার বলে উঠলেন, ‘তুমি একটা ভীতু। খুব ভীতু মেয়ে তুমি। স্বোপার্জিত স্বাধীনতা যখন ভাইঙ্গা ফেলতে চাইছিল, আমি একলা গিয়া দাঁড়াইছি টিএসসিতে। কোন বেটা আইবি এইটা ভাঙতে। সাহস থাকে তো আয়! কোনও শালা ধারে কাছে ঘেসার সাহস পায় নাই।’
শামীম সিকদার আমার দিকে ফেরেন। চোখে করুণা।
‘জুডো কারাতে কিছু জানো?’
‘না।’
‘কিছুই শিখো নাই জীবনে!’
‘ওইসব জানলেই কি! আমি তো মাঠে নেমে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি না।’
‘বুঝলাম। তোমার যুদ্ধ হইল ত তোমার কলম দিয়া। তারা তো শুধু কলম হাতে নেয় নাই। তারা আরও অনেক কিছু হাতে নিছে। পেশির জোর দেখাইতেছে। পুরুষের জোর দেখাইতাছে। রাস্তাঘাটে ভয়ে তুমি বার হইতে পারো না। এইটা কোনও কথা হইল! আরে দুই তিনটারে যদি ঘুসি দিয়া ফালাইয়া দিতে পারো, টুপি পাঞ্জাবি খুইলা ল্যাংটা কইরা ছাইড়া দিতে পারো, ওরা আর তোমার নাম মুখে নেবে না।’
শামীম সিকদারের মত সাহসী হওয়া আমি জানি আমার পক্ষে সম্ভব নয় কোনওদিন। সবাই শামীম সিকদার হতে পারে না। শামীম সিকদার বাংলাদেশে একজনই। ভয় ভীতি লজ্জা শরম, পাছে লোকে কিছু বলে এসবের তোয়াককা তিনি কোনওদিনই করেননি। অসম সাহসী মানুষটির পাশে বসার সুযেগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মানি।
খবরের কাগজ, আজকের কাগজ, সমীক্ষণ, ভোরের কাগজ, অনন্যা, যায় যায় দিনে আমার কলাম নিয়মিত ছাপা হচ্ছে। ইস্তফার পর এখন দুহাতে লিখছি। যায় যায় দিন এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক কাগজ। সম্পাদনা করেন শফিক রেহমান। শফিক রেহমান অনেককাল লণ্ডনে ছিলেন, সম্প্রতি দেশে ফিরে পত্রিকা বের করছেন। এরশাদ আমলে একবার তাঁকে দেশে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ঢাকা বিমানবন্দর থেকেই ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এরশাদের পতন ঘটার পর তিনি দেশে এসে দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছেন। যায় যায় দিনে শফিক রেহমানের অনুরোধে কলাম লিখি, কিন্তু লিখে স্বস্তি পাই না। কারণ ধর্ম নিয়ে কোনও বাক্য লিখলে তিনি দিব্যি তা উধাও করে দেন। আজকাল এরকম হচ্ছে প্রায় সব পত্রিকায়। মৌলবাদ নিয়ে লেখো, সে চলবে। কিন্তু ধর্মকে আক্রমণ কোরো না। আগে যেমন ইচ্ছে লিখতে পারতাম পত্রিকায়। কোনও রকম কাটছাট করা হত না। এখন দেখছি লেখার স্বাধীনতা অল্প অল্প করে লোপ পাচ্ছে। কোনওরকম অনুমতি না নিয়ে পত্রিকার সম্পাদকরা আমার লেখা থেকে বাক্য উড়িয়ে দেন, শব্দ ফেলে দেন। লেখাকে কেটে পঙ্গু বানিয়ে তারপর পাঠকের জন্য পরিবেশন করেন। ভোরের কাগজে বেদ বাইবেল ও কোরানের নারী বলে ধারাবাহিক একটি রচনা লিখছিলাম, সেটিও হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল। বন্ধ করার কারণ হল ধর্ম। ধর্ম ছাড়া অন্য যে কোনও বিষয় নিয়ে লিখতে পারি, এতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। ধর্মের আক্রমণে দেশ ধ্বংস হচ্ছে, কিন্তু ধর্ম নিয়ে মন্তব্য করা যাবে না। আমার লেখা ছাপা হলে নাকি পত্রিকার কাটতি বেড়ে যায়, সে কারণেই লেখার জন্য চাপ অনুরোধ আসে। আমি জানিনা কতটুকু কে বিশ্বাস করে আমি যা লিখি তা, কিন্তু কাটতি বাড়ে বলে এখনও আমাকে বহিস্কার করার সাহস পাচ্ছেন না। একবার রোববার পত্রিকার সম্পাদক সাজু আহমেদ আমার কাছে একটি লেখা চাইলেন, দিলাম, বেশ যত্ন করে ছাপলেন। এরপর আবার লোক পাঠালেন চিঠি দিয়ে, তাঁর আবদার আমি যেন নিয়মিত লিখি তাঁর পত্রিকায়। নিয়মিত আমাকে অনেকগুলো পত্রিকায় লিখতে হয়, তাই আমি সবিনয়ে জানিয়ে দিলাম, আমার সময় হবে না। আশ্চর্য এর কিছুদিন পরই তিনি আমার ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা রোববার বের করলেন। পঈচ্ছদে আমার ছবি, ভেতরে পাতায় পাতায় ছবি। পুরো রোববার জুড়ে যত লেখা আছে, তার প্রতি বাক্যে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা। কুৎসা যে এত নোংরা হতে পারে, অবমাননা যে এত অকরুণ হতে পারে, অসম্মাননা যে এত ভয়ংকর হতে পারে, হিংসা যে এত মারাত্মক হতে পারে, আগে আমার তা জানা ছিল না। ইসহাক খান রুদ্রর সেই বন্ধুটি, লেখাটি লিখেছেন। লেখার বিষয় আমার লেখালেখি নয়, বিষয় আমার যৌনজীবন। এ যাবৎ কত পুরুষের সঙ্গে আমার যৌনসম্পর্ক হয়েছে, কবে কোথায় কিভাবে সেসবের বিস্তারিত বানানো বর্ণনা। রুদ্রর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার আগেও নাকি ময়মনসিংহে আমার প্রেমিক ছিল, যার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ছিল আমার, ইত্যাদি গল্প। সেই যে কলেজ জীবনে কিছুদিন বিচিত্রায় ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বিভাগটি চালু হওয়ার শুরুতে কিছু বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, সে কথাও উল্লেখ করেছেন, কারণ আমার বিজ্ঞাপন বলে চালিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু অশ্লীল বাক্য তিনি রচনা করবেন। করেছেনও। পাঠক তো আর ষোলো বছর আগের বিচিত্রা খুঁজে দেখতে যাবে না সত্যিই আমি ওরকম বিজ্ঞাপন লিখেছিলাম কি না। ইসহাক খানের মাথায় এত যে কুবুদ্ধি তা লোকটিকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। গোবেচারা ধরনের চেহারা। জীবনে তাঁর স্বপ্ন ছিল গল্পকার হওয়ার, হতে পারেননি। এখন সাজু আহমেদের কল্যাণে গল্পকার হলেন বটে। চরিত্র হননের রগরগে গল্পখানা খুব বিকোলো। রোববারের সেই সংখ্যাটি তিনবার ছাপতে হয়েছে পাঠকের তাগাদায়। আমার ওপর প্রশংসা থাকলেও পত্রিকা চলে, নিন্দা থাকলেও চলে। দু হাজার বিক্রি হত রোববার, দুলক্ষ বিক্রি হয়ে গেল পলকে। সুতরাং প্রশংসার প্রয়োজন কী। নিন্দা দিয়েই ভরে ফেলা হোক না কাগজ! ব্যর্থ গল্পকার ইসহাক খান এই গল্পখানি লিখেই জীবনে প্রথম গল্পকার হিসেবে সাফল্য অর্জন করলেন। জীবন তাঁর সার্থক হল। কচুরিপানার মত অগুনতি পত্রিকা গজিয়েছে দেশে, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বিমাসিক, ষৈনমাসিক। কম চলা পত্রিকাগুলো বেশি চলার লোভে তসলিমার গল্প তৈরি করে ছাপে। পঈচ্ছদে পঈচ্ছদে তসলিমার ছবি, ভেতরে কত গল্প কত কাহিনী। আমার সঙ্গে কোনও সাংবাদিকের সাক্ষাৎ ছাড়াই, কোনও বাক্যালাপ ছাড়াই আমার বড় বড় সাক্ষাৎকার ছেপে ছাপা হয়ে যায়। ফতোয়া নিয়েও কত রকম মজা করা হয়। হাবীবুর রহমান নাকি বলেছেন আমাকে বিয়ে করতে চান তিনি। উত্তরে আমি নাকি বলেছি হ্যাঁ আমি রাজি। এদিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের মাথাটি নিয়ে মাথার ঠিক নেই। আর ওদিকে হা হা, ওদিকে হি হি।
মতিউর রহমান চৌধুরির উদ্দেশ্য ছিল আমাকে ঘৃণা করার পরিমাণ কত তীব্র এ দেশে, তা ফতোয়ার ঘটনাটি দিয়ে প্রমাণ করা। কিন্তু বুদ্ধিজীবিরা যখন বিবৃতি দিলেন আইনবিরুদ্ধ ফতোয়ার বিরুদ্ধে, প্রচুর লেখালেখি শুরু হল দেশে এবং বিদেশে, আমার পক্ষে জনমত গড়ে ওঠার ভাল একটি সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে আঁচ করে খানিক বিপাকে পড়েই হাবীবুর রহমান যে এরকম কোনও ফতোয়া দেননি অথবা দিলেও তিনি তা তুলে নিয়েছেন বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাবীবুর রহমান ফতোয়া তুলে নেওয়ার লোক হবেন কেন! তাঁর ডাকে গোটা সিলেটে অত্যন্ত চমৎকার ধর্মঘট পালন হয়েছে। ফতোয়ার কথাটি আপাতত উহ্য রেখে হাবীবুর রহমান জোর আন্দোলনে নেমেছেন। বিশাল বিশাল জনসভায় গরম গরম বক্তৃতা করছেন। ‘কুখ্যাত তসলিমা নাসরিনের সকল লেখা বাজেয়াপ্ত, তাকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতেঞ্চ সর্বস্তরের উলামা- মাশায়েখগণের উদ্যোগে ঢাকার সিসিলি রেস্তোরাঁয় একুশে অক্টোবর একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন হয়। সম্মেলনে সাংবাদিকদের উদ্যেশে বলা হল, ঞ্ছতসলিমা নামটি দেখে মনে হয় সে মুসলমান-সন্তান। অথচ, তার আকীদা, বিশ্বাস, মন – মানসিকতা সম্পূর্ণ বিপরীত। সে পবিত্র কোরান, মহানবী (সাঃ) এবং ইসলামী শরিয়তের বিরুদ্ধে জঘন্য কটুক্তি করে খোদাদ্রোহিতায় লিপ্ত রয়েছে। … তসলিমার নির্লজ্জ, ঔদ্ধত্যপূর্ণ অত্যন্ত আপত্তিকর লেখনির ফলে সমাজে, রাষ্ট্রে, দেশ ও বিদেশে অশ্লীলতা, বেলেল্লাপনা ও নগ্নতা মহামারির মত ছড়িয়ে পড়ছে। এতে করে দ্বীন ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) এর ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে। উক্ত মহিলা পবিত্র কোরানের সূরা আলে এমরান, সুরা নিসা, সুরা বাকারা, সুরা হুজরাত, সুরা ওয়াকিয়া, সুরা আররাহমান ইত্যাদি নাম ধরে ধরে আল্লাহর বিধানের প্রতি ব্যঙ্গ করেছে, কটুক্তি করেছে। অনুরূপভাবে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি জঘন্য ভাষায় কটাক্ষ করেছে। পবিত্র ধর্ম বিশ্বাসকে সে ভুল বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করেছে। সে আরো উক্তি করেছে, ধর্ম মানুষকে অমানুষ করে। ধর্ম নারীকে অপমানিত ও কুৎসিত করেছে। সে নারী নির্যাতন, নারী পুরুষে বৈষম্য ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কে দায়ী করেছে। ধর্ম বিশ্বাসীগণের প্রতি জঘন্য কটাক্ষ করে লিখেছে, যে সব নারী মহানবী (সাঃ) এর হাদীস মান্য করে আমি তাদের ধিককার না দিয়ে পারি না ইত্যাদি। যৌনাচার, ব্যাভিচার সকল ধর্মেই একটি ঘৃণ্য পাপ, অথচ তসলিমা নারী সমাজকে অবাধ যৌনতা ও ব্যাভিচারের প্রতি উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে লিখেছে, আমার মনে হয় একটি নারী ১০টি পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রেখেও সতী থাকতে পারে। এধরণের লাগামহীন বক্তব্য প্রকাশ এবং সমাজে এগুলি ব্যাপকভাবে প্রচার করার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। একটি কথা সর্বজন বিদিত যে, যদি কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহি বলে প্রমাণিত হয়, সে যদি প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তবে তার একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। ঠিক তেমনিভাবে মুসলমান নামধারী কোনও ব্যক্তি যদি দ্বীন ইসলাম, পবিত্র কোরান এবং মহানবী (সাঃ) এর প্রতি কটাক্ষ করতঃ দুর্নাম রটনা করে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস চালায় তবে সে ধর্মদ্রোহী, শরিয়তের বিধান মতে তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড।ঞ্জ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সাহাবা সৈনিক সমিতি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে যে, সিলেটে তারা সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল এবং অর্ধদিবস হরতাল পালনের মাধ্যমে সরকারের কাছে তিন দফা দাবি পেশ করেছে, ঞ্ছ১. অবিলম্বে তসলিমা নাসরিনকে গ্রেফতার, ২. তার সকল লেখা বাজেয়াপ্ত এবং ৩. তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান। এ দাবি তওহিদি জনতার প্রাণের দাবি। সরকারকে এ সব ন্যায্য দাবি মানতেই হবে। তসলিমার লজ্জা বইটি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে, অথচ লজ্জার চেয়ে বহুগুণ আপত্তিকর অন্যান্য বইগুলো বাজেয়াপ্ত করে সাহাবা সৈনিক পরিষদের ন্যায্য দাবি যেন মেনে নেওয়া হয়। আর বাংলাদেশে দ্বীন ইসলাম, পবিত্র কোরান এবং মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে কটুক্তি করার জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান চালু করার দাবিতে ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।ঞ্জ হবে কেন, হচ্ছে। আমি ষ্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আন্দোলন কেবল দানা বাঁধছে না, বীভৎস রূপ ধারণ করছে।
মিছিল আসছে। একশ নয়, দুশ নয়, কয়েক হাজার লোকের মিছিল। কাকরাইলের মোড় থেকে মিছিল আসছে শান্তিনগরের দিকে। আমি জানালায় বসে দেখছি বড় বড় অক্ষরে ব্যানারের লেখা, তসলিমার ফাঁসি চাই। এগিয়ে আসছে মিছিল নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর বলতে বলতে। মিছিল আসছে। মা বিড়বিড় করে সুরা পড়ছেন। আমাকে জানালার কাছে দেখে সুরা উবে গেল মুখ থেকে। টেনে আমাকে সরালেন জানালা থেকে। সুরায় খুব কাজ হবে বলে মার বিশ্বাস হয় না, মা দৌড়ে গিয়ে জায়নামাজে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাথা ঠেকিয়ে রাখলেন, যদি মার প্রার্থণা আল্লাহতায়ালার কানে পৌঁছোয়। আল্লাহ তায়ালা এই জনরোষ থেকে আমাকে যেন রক্ষা করেন। মিছিল এসে থামল শান্তিনগরের মোড়ে। মোড়ে কিছু খাকি পোশাকের পুলিশ দাঁড়ানো। পুলিশ বাধা দিচ্ছে এগোতে। মোড় থেকে নারায়ে তকবীরের গর্জনে বাড়ি কেঁপে ওঠে।
এরকম প্রায়ই মিছিল আসে বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে শান্তি নগরের দিকে। এরকম প্রায়ই প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকি।
মানুষের এই ঢল যদি কখনও আমার ঘরে উঠে আসার সুযোগ পায়! দরজায় বসে থাকা দুটো পুলিশ কি আর রোধ করতে পারবে ঢল! দিন দিন বানের ফুঁসে ওঠা জলের মত এগোচ্ছে মিছিল।
শায়খুল হাদিস বিখ্যাত লোক। তিনি নতুন একটি কমিটি গঠন করেছেন। ধর্ম ও দেশ বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটি। দলে দলে মুফতী মাওলানা যোগ দিচ্ছেন এই কমিটিতে। বিশাল ব্যানার নিয়ে বিশাল মিছিল করছে এই দল। বিশেষ করে শুক্রবার জুম্মাহর নামাজের পরই মিছিল শুরু হয়। কেবল মিছিল করেই বসে থাকে না এই দল। জাতীয় সংসদের স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে।
মাননীয় স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
সংসদ ভবন
শেরে বাংলা নগর,
ঢাকা
জনাব,
যথাযথ সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে
১. বাংলাদেশের আপামর জনতা গভীর ভাবে ধর্মপ্রাণ এবং এ দেশের সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ জনগণ যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যপারে অত্যন্ত সচেতন ও যত্নশীল এ সত্য সর্বজনবিদিত। কিন্তু কতিপয় বিভ্রান্ত মহল জনগণের ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানাকে প্রগতিশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন মনে করে জনগণের ধর্মীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের হীন তৎপরতা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ হেন দুষ্কর্মের পিছনে ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সামাজিক সুস্থিতির প্রতি বৈরি মহল সমূহের মদদ ও যোগসাজস রয়েছে তা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।
২. তসলিমা নাসরিন নাম্নী এক কুখ্যাত লেখিকা ক্রমাগত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কলাম, বই ও উপন্যাস লিখে একাধারে বাংলাদেশের সকল ধর্ম বিশ্বাসীর ধর্মীয় চেতনায় আঘাত হেনে চলছে। অন্যদিকে অত্যন্ত সুচতুর ও সুপরিকল্পিত ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারষ্পরিক বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে।
৩. মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যভিত্তিক অসৎ উদেবদশ্য প্রণোদিত উপন্যাস লজ্জা লিখার মাধ্যমে তসলিমা নাসরিন এ দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সর্বজন স্বীকৃত ঐতিহ্যে কালিমা লেপন করে আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে এবং দেশী বিদেশী কতিপয় সাম্প্রদায়িক মহলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা পরায়ণতার দিকে উস্কে দিয়েছে। অথচ সরকার শুধুমাত্র লজ্জা উপন্যাসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কোনরূপ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যদিও তসলিমা নাসরিনের বিভিন্ন লেখায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে বহু উস্কানিমূলক বক্তব্য রয়েছে যা সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল। সরকারের এহেন আচরণে দেশপ্রেমিক জনগণ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ ও হতাশাগ্রস্থ।
৪. যদিও সাংবিধানিকভাবে এবং দেশের প্রচলিত আইনে বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানা এবং তাদের মধ্যে পারষ্পরিক বিদ্বেষ ছড়ানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ কিন্তু এ ধরনের দেশ ও ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান না থাকায় দেশদ্রোহী ও ধর্মবিরোধী মহল সমূহ বেপরোয়া ভাবে অপকীর্তি চালিয়ে যাচ্ছে এবং সামাজিক সংঘাত ও অস্থিরতার ইন্ধন যোগাচ্ছে।
৫. বাংলাদেশের শতকরা নব্বইভাগ মানুষ মুসলমান। লেখিকা তসলিমা নাসরিন তার বিভিন্ন বই ও লেখার মাধ্যমে মুসলমানের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন, নবী(দঃ)এর হাদিস এবং ইসলামী শরিয়তের বিভিন্ন বিধি বিধানের প্রতি অবমাননামূলক কটাক্ষ প্রতিনিয়তই করে চলেছে এবং তার এহেন ধর্মদ্রোহী আচরণের বিরুদ্ধে দেশের প্রতিনিধিত্বশীল সকল ধর্মীয় মহল থেকে জোর প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সরকার এ ব্যপারে দুর্বল আইনের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে রহস্যজনক ভাবে নিষিক্রয়তার পথই অবলম্বন করে চলেছেন। ফলে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণেই বর্তমান আইন কানুন ও সরকারের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছেন।
৬. লেখিকা তসলিমা নাসরিন শুধু ধর্মের উপরেই আঘাত হানছে না, সমাজে প্রচলিত সার্বজনিন মূল্যবোধের বিপরীতে ব্যভিচার, অবাধ যৌন সম্পর্ক, বিবাহপূর্ব এবং বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক, নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক জুলুমের ফাঁপানো ফুলানো কল্পকাহিনী প্রচার করে সামাজিক সুস্থিতি বিনষ্টের অপপ্রায়াসেও লিপ্ত রয়েছে। তার লেখা যে পর্নোগ্রাফির পর্যায়ে পড়ে এবং তা এ দেশের যুব সমাজকে উμছৃঙ্খলতা ও নৈতিক অক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বৈ ত কিছুই নয়।
এমতাবস্থায় আমরা দেশ প্রেমিক ও ধর্মপ্রাণ মানুষের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে জোর দাবী জানাচ্ছি যে ১. দেশদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী মুরতাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড সহ কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা সম্বলিত আইন প্রণয়ন। ২. তসলিমা নাসরিনকে অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং ৩. তার যাবতীয় আপত্তিকর লেখা বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
(শাইখুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক)
আহবায়ক
ধর্ম ও দেশ বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটি
সাত মসজিদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
প্রায় একইরকম চিঠি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও দেওয়া হয়। ‘জনাব, আমরা অত্যন্ত হতাশা ও ক্ষোভের সাথে আপনার সমীপে নিবেদন করছি যে বাংলাদেশের বারো কোটি দেশপ্রেমিক ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস ও আবেগ অনুভূতিতে আবমাননাসূচক আঘাত হেনে তসলিমা নাসরিন নাম্নী এক কুখ্যাত লেখিকা….।’
লেখকের মাথার মূল্য ধার্য করা হয়েছে বাংলাদেশে। এ খবরটি বিশাল খবর, বিশেষ করে ইওরোপ আমেরিকায়। সালমান রুশদির ঘটনার পর এরকম একটি খবর লুফে নেবে বটে বিদেশের প্রচার মাধ্যম। একজন লেখক তাঁর লেখার কারণে ফতোয়ার শিকার হয়েছেন। মৃত্যুদণ্ডের দাবি তুলছে মুসলিম মৌলবাদীরা। রাজপথে মিছিল হচ্ছে। এমন সব খবর পড়ে লেখকের মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বিদেশের মানুষ। ইওরোপে আমেরিকার বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে মানবাধিকার কর্র্মী, লেখক সমাজ, নারীবাদী দল। বিভিন্ন বিদেশী সংগঠন থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে, আমাকে যেন নিরাপত্তা দেওয়া হয়, মৌলবাদীদের যেন দমিয়ে রাখা হয়। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় উপ সম্পাদকীয় লেখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ইংরেজিতে দুটো কথা না হয় চলে, তাই বলে লেখা! বলে দিতে নিই আমার পক্ষে অসম্ভব। তখন অসম্ভব কে সম্ভব করার জন্য এপির সাংবাদিক ফরিদ হোসেন এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে ফরিদ হোসেন বেশ অনেকবার যাওয়া আসা করেছেন আমার বাড়িতে, বিদেশি পত্রিকা থেকে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমার খবরাখবর নেওয়ার জন্য। ফরিদ হোসেন সুশিক্ষিত সাংবাদিক, অত্যন্ত ভদ্র, অমায়িক, আন্তরিক। কেবল সাংবাদিক হিসেবে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন না, দুঃসময়ে বন্ধুর মত পাশে দাঁড়াতেও আসেন। উপসম্পাদকীয়টি আমি বাংলায় লিখি, ফরিদ হোসেন আমার বাংলার ইংরেজি করে দেন। ডাক্তার রশীদ ঢাকা মেডিকেল থেকে সিলেটের মৌলভীবাজারে বদলি হয়ে যাওয়ার পর মাঝে মধ্যে ঢাকায় এলে আমার বাড়িতেই ওঠেন, আমার লেখার ঘরে তাঁর শোবার জায়গা করে দেওয়া হয়। তিনি দাদার মত উপদেশ বর্ষণ করে চলেন, দাদার মত বিদেশী সংগঠন থেকে আসা জরুরি চিঠিপত্রের উত্তর লিখে দেন। আন্তর্জাতিক লেখক সংগঠন পেন থেকে আমার খোঁজ করা হচ্ছে। খোঁজ করছেন মেরেডিথ ট্যাক্স। দিনে দশবার করে ফোন করছেন আমার বাড়িতে। প্রথম ফোন ধরে ইংরেজির আগা মাথা কিছু না বুঝে ফোন রেখে দিই। এরপর মেরেডিথ ট্যাক্সের ফোন এলে অন্য কাউকে ধরতে বলে আমি বাড়িতে নেই অথবা ঘুমোচ্ছি এই জাতীয় কিছু বলে দিতে বলি। মেরেডিথ কোত্থেকে আমার ফোন নম্বর যোগাড় করেছেন, তা সাধ্য নেই জানার। শেষ পর্যন্ত তিনি আমার উকিল কে সেই খোঁজ নিয়ে ডক্টর কামাল হোসেনের ওপর ফোন ফ্যাক্সের তুফান বইয়ে দেন। পেন এর লেখিকা শাখার সভানেত্রী মেরেডিথ, তাঁর দায়িত্ব পৃথিবীর কোথাও কোনও লেখিকার ওপর কোনওরকম আক্রমণ এলে তাঁকে সাহায্য করা! মেরেডিথ আমাকে আর কী সাহায্য করতে পারেন নিউ ইয়র্কে বসে! সরকারি দপ্তরে যত বিদেশি আবেদন অনুরোধ এসেছে, আমি নিশ্চিত, সবই ময়লা ফেলার ঝুড়িতে চলে গেছে। এসবের দিকে আমাদের পুতুলবিবি মোটেও ফিরে তাকান না। ফোন আসছে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, কানাডা, ইংলেণ্ড, ভারত নানা দেশ থেকে। আমি কেমন আছি, কী করছি, কী ভাবছি, নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি কি না জানার জন্য। ফোনে আশ মেটে না তাঁদের। উড়ে আসেন দূর দূর দেশ থেকে। প্রথম বিশ্ব হুমড়ি খেয়ে পড়ে তৃতীয় বিশ্বে। টেলিভিশন, রেডিও আর পত্রপত্রিকার সাংবাদিকের ভিড় লেগে গেছে আমার বাড়িতে। বিবিসি থেকে সাক্ষাৎকার নিয়ে গেল। তথ্যচিত্রও বানাচ্ছে বিবিসি। জার্মানির টেলিভশন থেকে লোক এল, কেবল সাক্ষাৎকার নয়, আরও কিছু চাই। পুরো একটি তথ্যচিত্র বানানোর জন্য যা কিছু প্রয়োজন। ফ্রান্স থেকে এল দুঘণ্টার একটি তথ্যচিত্র বানাতে। সেদিন আমার বাড়িতে শিবনারায়ণ রায় ছিলেন, সালমান রুশদির সঙ্গে আমার তুলনার প্রসঙ্গ এলে শিবনারায়ণ দৃঢ় কণ্ঠে বলে দিলেন, ‘সালমান রুশদি আর তসলিমার মধ্যে বিস্তর তফাৎ। সালমান রুশদি সমাজ পরিবর্তনের জন্য কোনও আন্দোলন করছেন না। তসলিমা করছেন।’ তথ্যচিত্রের দলটি এর পর সিলেটের হাবীবুর রহমানের সাক্ষাৎকার নিতে যায়, নিতে যে যাচ্ছে সে কথাটি আমাকে পুরো গোপন করেছে। এমন সতর্কতা। কিন্তু দলটির ছবিসহ ছাপা হয়ে যায় ইনকিলাবে। পুরোনো ঢাকায় নাকি কোনও এক হিন্দু পরিবারের সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছিল ওরা। গোয়েন্দা পুলিশের দল পিছু নিয়েছে ওদের। সরকারের ধারণা বিদেশীরা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তথ্যচিত্র করতে এসেছে। ইনকিলাবের আহবানে সরকার সেই দলের ওপর চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে দলটিকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। অতি সতর্কতায় তথ্যচিত্রের ক্যাসেটের একটি কপি ওরা আগে ভাগেই ফরাসি দূতাবাসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছিল প্যারিসে। কত কি যে ঘটে যায় আমার অজান্তে! আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসা কোনও বিদেশীকেই এখন থেকে আর দেশে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বুদ্ধিমান সাংবাদিকরা অন্য কোনও কারণের কথা বলে দেশে ঢুকছে। ফ্রান্সের ল্য-মন্দ পত্রিকা থেকে ক্যাথারিন বেদারিদা এলেন। লিবারেশন পত্রিকার আন্তোয়ান দ্য গুডমার। গুডমারকে খুব ভাল লাগে আমার। ফরাসিদের ইংরেজি বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না, ধীরে ধীরে বলেন ওঁরা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি। আমি তো আপাদমস্তক বাঙালি, ফরাসির তো প্রশ্ন ওঠে না, ভাল করে ইংরেজি না জানা বাঙালি, আমার ইংরেজিও অমন ভাঙা ভাঙা। গুডমারকে নিয়ে একদিন গাড়ি করে ধলেশ্বরী নদীটি দেখিয়ে আনি। গুডমার বললেন, ‘এই যে বাইরে বেরোচ্ছে!, কোনও অসুবিধে হয় যদি!’ আমি বললাম, ‘ঘরে বসে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে করে বাইরে বেরোতে।’ ফরাসি ফটো এজেন্সি থেকে যখন জিল সসেয়ার এলেন ছবি তুলতে, তাঁর অনুরোধে আমাকে ময়মনসিংহে যেতে হয়। জিলের খুব ইচ্ছে ময়মনসিংহের বাড়িতে যেখানে আমার শৈশব কৈশোর কেটেছে, যে ইশকুলে ছোটবেলায় পড়েছি, সেসবের ছবি নেওয়ার। এই যে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়া, যদিও হেঁটে নয়, রিক্সায় নয়, যদিও রাস্তাঘাটে দোকানপাটে, লোকের ভিড়ে, বাজারে থামা নয়, তারপরও আমার ভাল লাগে বেরোতে। গাড়ির জানালা দিয়ে অন্তত মানুষ দেখা যায়। ঘরের চার দেওয়ালের ভেতর বন্দী থাকতে থাকতে মনে হয় আমার বুঝি কবর হয়ে গেল ওখানেই। মরে তো যাবই একদিন, তাই বলে কি কবরে বসে কবরের দিন গুনতে হবে! শামীম সিকদারের ভয় পাবা না উপদেশটি বারবারই নিজেকে বলি।
ভারতের সানডে ম্যাগাজিন, স্টেটসম্যান থেকে সাংবাদিক আসেন সাক্ষাৎকার নিতে। সারা ভারতেই ফতোয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়ে সভা হচ্ছে। বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে। সচেতন লেখকরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন লিখে। পত্রিকায় সম্পাদকীয় যাচ্ছে। কলকাতায় অন্নদাশংকর রায়ের নেতৃত্বে লেখকরা গিয়েছেন বাংলাদেশ দূতাবাসে স্মারকলিপি নিয়ে। দূতাবাসের দুয়ার খটাশ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওঁদের মুখের ওপর। কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির আয়োজনে আমার জীবন ও লেখার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সভা হয়। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা অনুষ্ঠানে ছিলেন, অবশ্য বাংলাদেশের কেউ ছিলেন না। অন্নদাশংকর রায় ওখানেও ছিলেন। তাঁর মতে আমি একবিংশ শতকের কন্যা, ভুল করে বিংশ শতকে জন্মেছি। আমি ফ্রান্স বা ইংলেণ্ডের কন্যা, ভুল করে বাংলাদেশে জন্মেছি। আরেকটি কথা বলেছেন, ‘তসলিমা একজন আ্যংরি ইয়ং উওম্যান, মোল্লারা একদল অ্যাংরি ওল্ড ম্যান। এদের মধ্যে মিটমাট অসম্ভব। অনেক কথার মধ্যে আরেকটি কথা, বাংলাদেশের জনমত আমরা এখান থেকে বদলাতে পারব না, সেটা পারবে সেখানকার জননায়ক বুদ্ধিজীবীরা, আমরা তাঁদের সমর্থন করতে পারি শুধু।’
এদিকে পেঙ্গুইন ইণ্ডিয়া থেকে লজ্জার ইংরেজি সংষ্করণ বেরিয়ে গেছে। ফোন আসছে বিভিন্ন দেশ থেকে, প্রকাশকরা ফোন করছেন। তাঁরা লজ্জা বইটি অনুবাদ করে ছাপতে চান। ফতোয়ার খবরটি বিদেশের প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার পর ওখানকার মানুষের বদ্ধ ধারণা যেহেতু লেখক আমি, নিশ্চয়ই আমি এমন কোনও আপত্তিকর বই লিখেছি, যেটির কারণে মৌলবাদীরা আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছে। সালমান রুশদিকে ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল স্যাটানিক ভার্সেসএর কারণে। আমার ফতোয়াও নিশ্চয়ই কোনও না কোনও বইয়ের কারণেই। লজ্জা বইটি সরকার নিষিদ্ধ করেছে, সে অনেকদিন হয়ে গেল। কিন্তু সাংবাদিকরা পাকামো করে পাঠকের জানার তৃষ্ণা মেটাতে লজ্জাকে ফতোয়ার কারণ হিসেবে কোথাও কোথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লজ্জা কি মৌলবাদীদের ক্ষেপে ওঠার মূল কারণ? মোটেও না। ওরা তো ক্ষেপেই ছিল। ক্ষেপে আগুন হয়ে ছিল, সরকারের লজ্জা নিষিদ্ধের ঘি ওদের আগুনে গিয়ে পড়েছে। তাই ফতোয়া। আর ফতোয়ার বিরুদ্ধে সরকারের কিছু না করার ঘি ওদের আগুন আরও বেশি জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাই দেশ জুড়ে আন্দোলন। পেঙ্গুইন লজ্জা ছেপেছে, সে চলে। কারণ লজ্জার কাহিনী যদিও সম্পূর্ণ বাংলাদেশের পটভূমিতে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ যেহেতু ঘটে, পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না গল্পটি। কিন্তু জার্মান পাঠক বা ফরাসি পাঠক লজ্জার কী বুঝবে! আমি বিরক্ত কণ্ঠে প্রকাশকদের প্রশ্ন করি, ‘আপনারা কি জানেন লজ্জা বইটি কি নিয়ে?’
‘না, তা জানি না।’
‘এটা সম্পূর্ণ বাংলাদেশের স্থানীয় ব্যপার। প্রচুর তথ্য আছে। আপনাদের পাঠকের এসব পড়তে ভাল লাগবে না। উপন্যাস হিসেবে এটি ভাল কোনও বই নয়।’
‘সে নিয়ে আপনি মোটেও ভাববেন না। অনুগ্রহ করে আমাদের অনুমতি দিন।’
‘আমি এমন কোনও বই এখনও লিখিনি যেটি বিদেশে অনুবাদ হতে পারে। এখানকার সমাজের সমস্যা নিয়ে লিখি। কোনও বই আন্তর্জাতিক মানের নয়। আমি ভাল কোনও বই লিখি আগে, তারপর দেব আপনাদের।’
‘সে না হয় ছাপব, যা লিখবেন ভবিষ্যতে। কিন্তু আমরা লজ্জা ছাপতে চাইছি।’
‘কেন, লজ্জা কেন?’
‘লজ্জা তো বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করেছে। লজ্জার জন্যই তো ফতোয়া।’
‘না, লজ্জার জন্য আমাকে ফতোয়া দেওয়া হয়নি। লজ্জা বের হওয়ার আগে থেকেই আন্দোলন করছে মৌলবাদীরা। নিষিদ্ধ হওয়ার অনেক পরে ফতোয়া দিয়েছে। লজ্জা বের হওয়ার পর ছ মাস চলেছে এখানে। কোনও মৌলবাদী লজ্জা নিষিদ্ধ করার দাবি করেনি।’
‘তবুও আমরা লজ্জাই ছাপতে চাই।’
‘এ বই আপনাদের ওখানে চলবে না।’
‘সে আমরা বুঝব। লজ্জা বইটি ছাপার অনুমতি তো দিন। আমরা অগ্রিম রয়্যালটি দেব।’
রিয়্যালটি কোনও ব্যপার নয়। ব্যপার হচ্ছে পাঠকের আগ্রহ। এখানকার হিন্দু মুসলমানের সমস্যা নিয়ে ওখানে আগ্রহ থাকার কথা নয়।’
‘খুব আগ্রহ আছে। আপনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। এসব আমরা দেখব।’
নাছোরবান্দা। ফ্রান্সের এডিশন দ্য ফামের মিশেল ইডেল দিনে তিনবেলা ফোন করেন, ‘তসলিমা আপনি তো নারী স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছেন। এখানে আমাদের সংগঠনও দীর্ঘবছর ধরে একই সংগ্রাম করে আসছি। আমরা আপনার জন্য এখানে আন্দোলন করছি। আপনি আমাদের লজ্জা বইটি ছাপার অনুমতি দিন। আমরা কনট্রাক্ট ফরম পাঠাচ্ছি। আপনি সই করে দিন।’
‘দেখুন, লজ্জা বইটি নারী স্বাধীনতার ব্যপার নয়। নারী বিষয়ে আমার কিছু বই আছে। আপনারা দেখুন, ওর মধ্যে একটি ছাপা যায় কি না। যদিও আমি নিশ্চিত নই, বাংলাদেশের মেয়েদের সমস্যাগুলো আদৌ ওখানে..’
‘সে নিয়ে ভাববেন না। আমরা অন্য দেশের মেয়েদের সমস্যা জানতে চাই খুব। কিন্তু ওগুলোও ছাপবো। লজ্জা আগে ছাপবো।’
‘লজ্জা ইংরেজিতে ছাপা হয়েছে। আগে পড়ে দেখুন ওটি, ছাপার যোগ্য কি না। আমি কিন্তু জানি যে আপনি পড়ার পর ছাপতে রাজি হবেন না।’
‘না বলব! বলছেন কি? আমরা লজ্জা বইটা পাওয়ার জন্য এমন আকুল হয়ে বসে আছি।’
‘কি আছে ওতে বলুন তো?’
‘ওতে ইসলামের সমালোচনা করেছেন। তাই তো মুসলমানরা ক্ষেপেছে।’
আমি তিক্ত গলায় বলি, ‘সম্পূর্ণ ভুল। কোনওরকম ইসলামের সমালোচনা নেই ওতে।’
‘দেখুন তসলিমা, আমরা ধর্ম বিশ্বাস করি না। আমাদের কাছে সব ধর্মই এক রকম। সব ধর্ম দ্বারাই মেয়েরা নির্যাতিত।’
‘সে কথা তো আমিও মনে করি।’
‘আপনি মনে করবেন না যে ইসলামের সমালোচনা বলে আমরা ছাপতে চাইছি বই। একজন নারীবাদী লেখিকা সুদূর বাংলাদেশে কি বই লিখেছে, যার জন্য তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হয়েছে, সরকার সেই বই নিষিদ্ধ করেছে। আমরা সেই বই পড়তে চাই। আমাদের পাঠক চাইছে পড়তে।’
‘আবারও বলছি লজ্জার জন্য ফাঁসি চাইছে না কেন। ফাঁসি চাইছে ইসলাম বিষয়ে আমার মন্তব্যের জন্য।’
‘ওই হল। আপনার লেখার জন্য ফাঁসি তো চাইছে দিতে!’
চলছেই। যত চলছে তত আমি অপ্রতিভ বোধ করছি। ফরাসি দুই প্রকাশক, মিশেল ইডেল আর ক্রিশ্চান বেস দুজনই লজ্জা ছাপার জন্য আমার অনুমতি নেবেনই নেবেন। আমাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে দুজনের মধ্যে। দুজনেই কনট্রাক্ট ফরম পাঠিয়ে দিলেন। মিশেল ইডেল আমাকে দিতে চেয়েছিলেন পাঁচ হাজার ফ্রাঁ অগ্রিম। ক্রিশ্চান বেস বলছেন তিনি তিরিশ হাজার ফ্রাঁ দেবেন। প্রতিদিন ফোন আসে ফ্রান্স থেকে, আমি কণ্ঠ শুনেই পালাই। লজ্জা আমার জন্যই বড় একটি লজ্জা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী লাভ ফরাসি পাঠকদের এখানের ভোলার গ্রামে বা মানিকগঞ্জের কোনও এক অজপাড়াগাঁয়ে কি ঘটেছে তা জেনে! ক্রিশ্চান বেস হঠাৎ হঠাৎ পালিয়ে যাওয়া আমাকে খপ করে ধরে বলতে থাকেন ‘তসলিমা আপনি লেখক। অনেক প্রকাশক আছে ঝড় ওঠে যে বইটি নিয়ে সে বইটি ছেপে তারা লেখককে বেমালুম ভুলে যায়। কিন্তু আপনাকে আমরা সম্মান করি লেখক হিসেবে। আমরা ভাল লেখকের বই ছাপি, সে বই বিক্রি হোক বা না হোক। হঠাৎ নাম হওয়া কোনও লেখকের একটি বই হুজুগে ছাপা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পৃথিবীর বড় বড় লেখকের বই ফরাসিতে আমরা ছাপছি। আপনি যে অন্য ফরাসি প্রকাশকের কথা বলছেন, সেই প্রকাশক নারীবাদী বই ছাপে, আপনার লজ্জা তো নারীবাদী বই নয়। তবে কেন তারা ছাপতে চাইছে, চাইছে লজ্জা নিয়ে এখন পত্রিকায় লেখা হচ্ছে বলে।’
আমি বলি, ‘আমি যে ভাল লেখক, তা কি করে জানেন? আপনি তো আমার লেখা পড়েন নি! আসলে সত্যি কথা, আমি কিন্তু ভাল লিখতে পারি না। এ দেশে অনেক লেখক আছেন, আমার চেয়ে হাজার গুণ ভাল। আমি তো ডাক্তারি পড়েছি। বাংলা সাহিত্য আমার বিষয় ছিল না। উপন্যাস কি করে লিখতে হয় এখনও শিখিনি। মূলত দেশের সমস্যা টমস্যা নিয়ে লিখি। মাঝে মাঝে অন্যায় অত্যাচার বৈষম্য ইত্যাদি দেখে খুব রাগ করে লিখি, এই যা।’
ক্রিশ্চান বেস আপন আপন সুরে বলেন, ‘আপনি আপনার লেখাকে এত ছোট করে দেখবেন না। আপনি লিখতে পারেন না বলছেন, না পারলে এত লোক আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপেছে কেন? নিশ্চয় আপনি একটি আঘাত করেছেন। সেই আঘাতটি তো সকলে করতে পারে না। ভাল সাহিত্যের যেমন মূল্য আছে, তেমনি সমাজ পাল্টাবার জন্য খুব আঘাত করে লেখারও মূল্য আছে। আত্মবিশ্বাস রাখুন। আত্মবিশ্বাস থাকলে আপনি আরও ভাল লেখা লিখতে পারবেন। আপনার লেখক পরিচয়টি আপনি না চাইলেও এটিই আপনার পরিচয় এখন। আপনি লিখুন। আমরা প্রকাশকরা কেবল তো জনপ্রিয় আর বিখ্যাত লেখকের লেখা ছাপি না, আমরা লেখককে লেখার, আরও ভাল লেখার উৎসাহ দিই। এটিও আমাদের কাজ। আমরা লেখক তৈরিও করি। সম্ভাবনা যাদের মধ্যে আছে, তাদের আমরা প্রেরণা দিই। আপনার মধ্যে সম্ভাবনা আছে তসলিমা।’
বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। বাংলাদেশের আইনে ফতোয়া নিষিদ্ধ হলেও ইসলামে এটি নিষিদ্ধ নয়। ইসলাম দিয়েই দিয়েছে কিছু কিছু শাস্তির বিধান। অবৈধ সম্পর্কে করবে, পাথর ছুঁড়ে মারা হবে। অনৈসলামিক কাজ করবে, একশ একটা দুররা মারা হবে। মৌলবাদ জেগে উঠছে। হাওয়া এখন মৌলবাদিদের দিকে বইছে। গ্রামে গ্রামে ফতোয়াবাজ মাওলানাদের ফতোয়ার শিকার হচ্ছে মেয়েরা। সিলেটের ছাতকছড়া গ্রামে নূরজাহান নামের একটি মেয়ে দিতীয়বার বিয়ে করেছিল, যে বিয়ে, মাওলানা মান্নান বলেছেন ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ, কারণ নূরজাহানের সঙ্গে তার প্রথম স্বামীর তালাক হয়নি (প্রথম স্বামী তাকে ফেলে চলে গেছে বহু বছর আগে। দ্বিতীয় বিয়ের আগে নূরজাহান নিজে তালাকনামা পাঠিয়েছিল প্রথম স্বামীর ঠিকানায়)। সুতরাং নূরজাহানকে পাথর ছোঁড়া হবে। নূরজাহানের বাড়ির উঠোনে মাওলানারা একটি গর্ত খুঁড়লেন, ওতে নূরজাহানকে দাঁড়াতে হল। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে মাওলানারা পাথর ছুঁড়লেন নূরজাহানের গায়ে। পুরো গ্রাম দাঁড়িয়ে দেখল এই দৃশ্য, কোনও প্রতিবাদ করেনি কেউ। রক্তাক্ত, লান্থিত নূরজাহান গর্ত থেকে উঠে ঘরে গিয়ে লজ্জায় অপমানে বিষ পান করে আত্মহত্যা করে। এর পরপরই আবার আরেকটি ঘটনা, ফরিদপুরের একটি মেয়ে, এই মেয়ের নামও নূরজাহান, ঘরে স্বামী রেখে অন্য লোকের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল, পরপুরুষের সঙ্গে লীলা খেলা ইসলামে নিষিদ্ধ, সুতরাং মাওলানারা ফতোয়া দিলেন নূরজাহানের বিরুদ্ধে। নূরজাহানের হাত পা বেঁধে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল নুরজাহান। এর পরই সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থানার কালিকাপুর গ্রামে আরেকটি ঘটনা ঘটে। খালেক মিস্ত্রির ষোল বছরের মেয়ে ফিরোজা নদীতে চিংড়ি মাছের পোনা ধরে তা বিক্রি করে সংসারে সাহায্য করত। এই পোনা ধরতে গিয়েই তার সঙ্গে পরিচয় হয় পাশের বন্দকাটি গ্রামের জেলে হরিপদ মণ্ডলের ছেলে উদয় মণ্ডলের। উদয়ের সঙ্গে ফিরোজার সম্পর্ক গড়ায়। সম্পর্ক গড়ায় বলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরিয়ত অনুযায়ী ফিরোজার বিচার করে। ফিরোজাকে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে একশ একবার ঝাঁটাপেটা করা হয়। ঝাঁটা পেটা শেষ হলে ফিরোজা তার বোনের কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি পৌঁছেই আত্মহত্যা করে। উদয়ের জন্যও শাস্তির ব্যবস্থা হয়। হিন্দু বলেই হয়। গ্রামের সব ফতোয়ার খবর পত্রিকায় ছাপা হয় না। কারণ আটষট্টি হাজার গ্রামের কোন কোণে কোন মেয়েকে ফতোয়ায় মরতে হচ্ছে তা সহজ নয় জানা। হঠাৎ হঠাৎ কোনও ফতোয়া গ্রাম জুড়ে আলোড়ন তুললে হয়ত গোচরে আসে কোনও মফস্বলের সাংবাদিকের। তারপরও দেখতে হবে সেই সাংবাদিক কোন পত্রিকায় খবরটি দেবে। ইনকিলাব গোষ্ঠীর পত্রিকার লোকেরা এ জাতীয় খবর ছেপে ফতোয়াবাজদের ওপর জনগণের রাগ করার কোনও সুযোগ দেবে না। বরং খবর যদি অন্য পত্রিকায় প্রকাশ পায় এবং সমালোচনার ঝড় বয়, তবে ফতোয়াবাজদের পক্ষে এবং সেই সব নিরীহ মেয়েদের বিপক্ষে শক্ত শক্ত যুক্তি দাঁড় করিয়ে ফতোয়াকে বৈধ করার চেষ্টা করবে। দেশের সর্বাধিক বিক্রিত এবং বিকৃত পত্রিকা ইনকিলাব। একসময় ইত্তেফাকের ছিল সবচেয়ে বেশি বিক্রি, ইত্তেফাককে ছাড়িয়ে মাড়িয়ে গেছে ইনকিলাব। এদিকে আরেকটি ভয়ংকর খবর যখন প্রকাশ পায় যে ব্র্যাক (এনজিও)এর তৈরি একশ বারোটি মেয়েদের ইশকুল মৌলবাদিরা পুড়িয়ে দিয়েছে এবং মেয়েদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে যে এখন থেকে তাদের ইশকুলে যাওয়া বন্ধ, তখন ইনকিলাব দায়িত্ব নেয় ফতোয়াবাজদের পক্ষে গীত গাওয়ার। এনজিওর ইশকুলগুলো নাকি মেয়েদের খ্রিস্টান বানাবার চেষ্টা করছিল, যেহেতু ব্র্যাক খ্রিস্টানদের দেশ থেকে অর্থসাহায্য পায়। গ্রামের যে মেয়েরা এনজিওতে কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধেও ফতোয়া, ঘরের বাইরে বেরোনো চলবে না। যদি মেয়েরা এই ফতোয়া না মানে, তবে তাদের স্বামীদের বাধ্য করা হবে স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য। কেবল ফতোয়াই নয়, সালিশের বর্বরতাও সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গ্রামে সালিশ বসার নিয়ম চালু যুগ যুগ ধরে। মসজিদের ইমাম আর গ্রামের মাতব্বরের সালিশে সিরাজগঞ্জের বাদেকুশা গ্রামে পঁয়ত্রিশ জন মেয়েকে সমাজচ্যূত করা হয়েছে। তারা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, এই তাদের অপরাধ। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা মানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বিরোধিতা করা। সুতরাং পঁয়ত্রিশ জন মেয়েকে সমাজচ্যূত হয়ে বাকি জীবন বাস করতে হবে। ধর্মের কুঠার মেয়েদের মাথার ওপর, পঁয়ত্রিশ জন মেয়ের এখন আর সমাজে জায়গা নেই। নিঃশব্দে তাদের মেনে নিতে হয়েছে এই সালিশ। ধর্ম এখন মাওলানাদের বাপের সম্পত্তি। আলখাল্লা জোব্বা পরল, মাথায় টুপি লাগাল, নামাজ পড়ে পড়ে কপালে কালো দাগ করে ফেলল, তসবিহর গোটা নাড়ল চাড়ল, ধর্ম তাদের স্থাবর সম্পত্তি হয়ে গেল। ধর্মের ভয় দেখিয়ে তারা এখন পুরো দেশের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কোনও ফতোয়াবাজ মাওলানার বিরুদ্ধে, কোনও সালিশের ইমাম আর মাতববরের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে আদালতে কোনও মামলা করা হয় না। তাদের অপকর্মের জন্য কোনও শাস্তির ব্যবস্থা নেই।
এদিকে বড় শহরে জুসমে জুলুসের মিছিল হচ্ছে। ঘটা করে হযরত মোহাম্মদের জন্মদিন পালন হচ্ছে। বিশাল বিশাল টুপিবাহিনীর ট্রাক-মিছিলে পুরো ঢাকা শহর ছেয়ে যায়। সাজ সাজ রব চারদিকে। আর যেদিন হিন্দুদের জন্মাস্টমীর মিছিল বেরোলো, মিছিলে বিএনপির লাঠিয়াল বাহিনী আর যুব কমাণ্ডের লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মেয়েদের শাড়ি খুলে নিয়েছে, কৃষ্ণ সেজেছিল যে শিশুটি, তারও মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। পুলিশ কোনও আক্রমণকারীকে একটি টোকা পর্যন্ত দেয়নি। দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে শুধু।
যখন দেশজুড়ে মৌলবাদিদের প্রলয়ঙ্করী নৃত্য চলছে, তখন সরকার বিষম বিচক্ষণতা দেখালেন মৌলবাদিদের নেতা গোলাম আযমকে নিরপরাধ প্রমাণের ব্যবস্থা করে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে! ঘাতকের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে প্রকাশ্যে। যে দেশদ্রোহীর নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছিল, সেই দেশদ্রোহীকে আজ সসন্মানে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। কি জানি, সম্ভবত এই সরকার গোলাম আযম এবং তাঁর ঘাতক সঙ্গীদের, যাদের কারণে লক্ষ লক্ষ বাঙালির ঘর আগুনে পুড়েছে, লক্ষ লক্ষ বাঙালি নিহত হয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছে, অচিরে মুক্তিযোদ্ধার সনদ দেবে। গোলাম আযমকে মুক্তি দেওয়া হয় আর ওদিকে রমনায় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির গণআদালত এর সভা থেকে মাইক ছিঁড়ে নেওয়া হয়, গণসমাবেশে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, মানুষ আহত হয়। এ দেশ যেন আমার নয়, আমাদের নয়, আমরা যারা গর্ব করি রফিক বরকত, সালামকে নিয়ে, যাঁরা বাংলা ভাষার জন্য বাহান্নর ফেব্রুয়ারিতে প্রাণ দিয়েছিলেন, আমরা যারা গর্ব করি অসংখ্য অগুনতি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে, যাঁরা এ দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এ দেশ হয়ে যাচ্ছে গোলাম আযমের দেশ। উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ। শহীদ মিনারের পাশের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাস, কাজী নজরুলের বাণীগুলো রঙ মেখে নষ্ট করে দিয়েছে স্বাধীনতার শত্রুরা। কালি লেপে দিয়েছে ‘বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি।’র ওপর। আর কত ধ্বংস দেখতে হবে আমাদের! তার চেয়ে অন্ধ হয়ে যাক আমাদের চোখ, আমরা বধির হয়ে যাই!
গ্রামের মেয়েদের ওপর ফতোয়া দেওয়ার প্রতিবাদ করতে মহিলা পরিষদ একটি মিছিল বের করে। প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তায় বসে যান গ্রামের মহিলারা, হাতে কঞ্চি, কঞ্চির আগায় মহিলা পরিষদের স্লোগান লেখা কাগজ। মহিলা পরিষদের সভায়, কোন কোন মেয়েকে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে সবার নাম উল্লেখ করে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দেন নেত্রীরা। কেউ কিন্তু একবারও উচ্চারণ করেননি আমার নাম। মহিলা পরিষদ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নারী সংগঠন, সভানেত্রী হিসেবে সুফিয়া কামালের নাম থাকলেও মূল নেত্রী মালেকা বেগম। মালেকা বেগম নারী বিষয়ে অনেকগুলো বইও লিখেছেন। বহু বছর ধরে তিনি নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং বলা যায় দেশের হাতে গোণা দুইএকজন নারীবাদী নেত্রীর মধ্যে তিনি অন্যতম। একদিন আমার বাড়িতে তিনি পদধূলি দেন। বিস্ময়াভিভূত আমি তাঁকে প্রায় আলিঙ্গণ করতে নিই। পত্রিকায় কলাম লেখা শুরু করার পর মালেকা বেগমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কয়েকবার, বলেছিলেন, ‘খুব ভাল হচ্ছে লেখা, লিখে যাও, লিখে যাও।’ মালেকা বেগমের স্বামী মতিউর রহমান কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা একতার সম্পাদক। একতা থেকে বেরিয়ে এসে এখন অবশ্য ভোরের কাগজএর সম্পাদক হয়েছেন। দুজনই সমাজতন্ত্র বিশেষজ্ঞ। দুজনের প্রতিই আমার শ্রদ্ধা প্রবল। প্রবলই ছিল। তবে মাঝে মাঝে প্রবলের শরীরে চমকের ধাককা লেগেছে। আনন্দ পুরস্কার পাওয়ার পর অতি আনন্দে আনন্দর খবর দিতে যেদিন মালেকা বেগমের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তিনি বক্রহাসি হেসে বলেছেন, ‘সুনীলের সঙ্গে খাতির থাকলে আনন্দ পুরস্কার পাওয়াই যায়, এ তো সবাই জানে!’ তিনি মোটেও পছন্দ করেননি আমার পুরস্কার পাওয়া। আমি যোগ্য নই পুরস্কারের, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার জন্য এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন, এই তাঁর বিশ্বাস। বড় একা বোধ করেছি। আনন্দ পুরস্কার এমনই একটি ধারালো কাঁটা, যে কাঁটাটি আমার শুভাকাঙ্খীদের বড় একটি সংখ্যার শরীরকে খোঁচা মেরে প্রায় শূন্যে নামিয়ে দিয়েছে। আমি মাথা নিচু করে মালেকা বেগমের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। আরও একদিন অবাক লেগেছিল আমার, আমি বুঝে পাইনি মালেকা বেগম এ কী কাণ্ড করছেন, যখন তিনি তাঁর দলের লোক নিয়ে আদালত প্রাঙ্গনে খুকুর ফাঁসি চাইছিলেন। মুনিরের সঙ্গে খুকুর সম্পর্ক ছিল এবং সে সম্পর্ক ছিল অবৈধ, এ কথা পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার পর লোকেরা খুকুকে ছি ছি করল, দুয়ো দিল। আর কোথায় খুকুর পক্ষে দাঁড়াবে মহিলা পরিষদ, উল্টো আদালতের দরজায় গিয়ে খুকুর ফাঁসি চাই চিৎকার দিয়ে গলা ভাঙল। মহিলা পরিষদের বিখ্যাত নেত্রীটি এখন আমার বাড়িতে।
‘তোমাকে দেখতে আসলাম, কেমন আছ তুমি?’
আমি মলিন হাসি। আমি কেমন আছি তা নিশ্চয়ই তিনি অনুমান করতে পারেন।
‘তোমার কাছে আসলাম। ভাবলাম দেখে যাই। যে অবস্থা হচ্ছে দেশে, তোমার জন্য খুব চিন্তা হয় আমাদের। মোল্লারা খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।’
‘হ্যাঁ। কি যে হবে দেশের!’
মালেকা বেগম হঠাৎ হেসে ওঠেন, হাসির দিকে তাকিয়ে থাকি বিস্ময়ে। হাসি থামলে বলেন, ‘তিরিশ বছর ধরে নারী আন্দোলন করছি, আর দেশে বিদেশে নারীবাদী হিসেবে নাম হয় তোমার!’
নাম হওয়ার লজ্জায় আমি মুখ লুকোই। নাম হওয়ার মত অপমানকর ঘটনা যেন জগতে আর কিছু নেই। নাম হওয়াটিকে এই মুহূর্তে গলা টিপে হত্যা করতে পারলে আমার স্বস্তি হত। এ আমারই দোষ। আমার দোষেই আমার নাম লোকে জানে।
মালেকা বেগম খুব বুদ্ধিমতি, বুদ্ধিমতি না হলে আমার মনের কথা জানবেন কী করে! বললেন, ‘না, এতে তো তোমার দোষ নেই। মোল্লারাই তোমার নাম জানাচ্ছে।’
হেসে উঠলেন আবার, বললেন, ‘আসলে মনে মনে ওদের তোমার ধন্যবাদই দেওয়া উচিত।’
আমি আমার অস্বস্তি কাটাতে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই বলতে বলতে, ‘চা খাবেন তো! আমি চায়ের কথা বলে আসি।
চা খাওয়া শেষে তিনি যা বললেন, তা হল, ‘তসলিমা এ সময় তোমাকে আমরা সমর্থন করতে পারব মানে তোমার পক্ষে দাঁড়াতে পারব, তুমি যদি আমাদের সংগঠনে যোগ দাও।’
‘সংগঠনে? মহিলা পরিষদের সদস্য হতে বলছেন?’
‘হ্যাঁ।’
আমি হাঁ হয়ে থাকি কিছুক্ষণ।
‘মালেকা আপা, আমি মহিলা পরিষদে যোগ না দিলে বুঝি আমাকে যে ফতোয়া দেওয়া হল, এই যে আমার বিরুদ্ধে মোল্লারা আন্দোলন করছে, এর প্রতিবাদ করতে পারেন না! আপনারা মেয়েদের পক্ষে আন্দোলন করছেন, আমি মেয়েদের পক্ষে লিখছি..
‘আসলে তুমি তো একটু কনট্রোভার্সিয়াল!
‘তাতে কি? আমার পক্ষে আপনারা যদি কিছু না বলতে চান বলবেন না, কিন্তু একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ তো করা উচিত!’
মালেকা বেগম একসময় উঠে পড়েন তাঁর দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে। আমি যে মহিলা পরিষদের সমর্থন পেতে মহিলা পরিষদে নাম লেখাবো না, তা তিনি একরকম বোঝেন। তারপরও আমাকে ভাবার জন্য সময় দিতে চান। মালেকা বেগমের লেখা বেশ কিছু বই আমি পড়েছি, বই পড়ে একটুও মনে হয়নি কখনও কখনও তিনি আপোস করতে পারেন বা কোথাও কোথাও তিনি নগ্নভাবে যুক্তিহীন হতে পারেন।
ফ্রান্স থেকে রিপোর্টার্স সাঁ ফ্রন্টিয়ার্স আর আর্তে টিভি আমাকে প্যারিসে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল টেলিভিশনে প্রেস ফ্রিডমের ওপর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। প্যারিসের কথা কেবল লোকের মুখে শুনেছি, বইয়ে পড়েছি, কল্পনাও করিনি সত্যিকার প্যারিস যাওয়ার। লোকদের জানিয়ে দিই, আমার বাপু পাসপোর্টই নেই, আমার যাওয়া হবে না। যাওয়া হবে না এরকমই জানি। দেড় বছর হয়ে গেছে, আজও যখন পাসপোর্ট দেওয়া হয়নি আমাকে, কোনওদিনই দেওয়া হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয় আমাকে পাসপোর্ট। ফতোয়ার খবরটি বিদেশে প্রচার হওয়ার পর সবচেয়ে যে বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেছে, তা হল আমার পাসপোর্ট ফেরত পাওয়া। আমার নাগরিক অধিকার এবং মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে যখন বিদেশিদের আন্দোলন হচ্ছে, তখন একদিন আমেরিকার দূতাবাস থেকে অ্যান্ড্রু নামের এক অফিসার আমার বাড়ি এলেন। কি করে আমার পাসপোর্ট নিল, কবে নিল, কারা নিল ইত্যাদি খবর টুকে নিয়ে চলে গেলেন। আবারও একদিন এসে পাসপোর্টের কথাই বললেন। এরপর দু সপ্তাহও পার হয়নি, অ্যান্ড্রু আমাকে ফোন করে বললেন, পাসপোর্ট আপিসে গিয়ে আমি যেন আমার পাসপোর্টটি নিয়ে আসি। এমনতরো জাদু আমার আগে দেখা হয়নি। দেড় বছরে যে জিনিসটি আমার পক্ষে করা সম্ভব হয়নি, সে জিনিসটি কি করে নিমিষে সম্ভব করে ফেলে একটি দূতাবাস! পাসপোর্টটি হাতে নিয়ে আত্মহারা হই, দেশের বাইরে কোথাও যাওয়ার আনন্দে নয়, আমার নাগরিক অধিকার ফিরে পেয়ে।
ফতোয়ার খবর নিয়ে হুলস্থুল পড়ে গেছে সবখানে। বিদেশের বড় বড় পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে এই ফতোয়া নিয়ে। লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ করছেন। বিদেশের নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, লেখক সংগঠনের লোকেরা মরিয়া হয়ে উঠেছে আমাকে রক্ষা করতে। এক ফতোয়াই আমার নাম ফাটিয়ে দিল বিশ্বময়। কিন্তু যে ফতোয়ার খবরটি কেউ জানে না সেটি হল আমার মার ওপর ফতোয়া। পীরবাড়ি থেকে দেওয়া ফতোয়া। পীরবাড়ি ছিল মার আশ্রয়। খুব বড় আশ্রয়। দীর্ঘ দীর্ঘ বছর ধরে পীর বাড়িতে যান মা, আল্লাহ রসুলের কথা শুনে সংসারের দুঃখ কষ্ট খানিকটা ভুলে থাকতে যান। হাসিনার ওপর সংসারের দায়িত্ব অর্পিত হবার পর অবকাশে মা একটি বাড়তি মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হলেন। আমি যখন একা থাকতে শুরু করি ঢাকার শান্তিবাগে, আমার কাছে চলে এসে অবকাশের দুঃখও ভুলতে চাইতেন। আমার কাছেও যে খুব সুখ পেতেন তা নয়। ঢাকা থেকেও প্রায়ই পীরবাড়ির দিকে ধাবিত হতেন। এরপর ভালবাসার জন্ম হওয়ার পর অবকাশে মাস কয় কাটিয়ে ইয়াসমিন যখন ভালবাসাকে নিয়ে ঢাকা চলে আসে, সঙ্গে মা আসেন। কারণ মার ওপরই দায়িত্ব ভালবাসার লালন পালনের। ঢাকায় আসার পর মা দেখলেন বাচ্চার ক্যাঁও ম্যাঁও আমার লেখার অসুবিধে করে, আমার ঘুম নষ্ট করে, তার ওপর থাকার জায়গার অভাব। এসব কারণ তো আছেই, সবচেয়ে বড় যে কারণটির জন্য মা চলে গেলেন ময়মনসিংহে, তা আবারও সেই একই কারণে, খরচ বাঁচাতে। আমার হোক, ইয়াসমিনের হোক খরচ তো কারও না কারও করতেই হবে, বাচ্চা পোষার খরচ তো আর সামান্য কিছু নয়! সুহৃদের জন্মের পর সুহৃদের দায়িত্ব মার ওপর ছিল, লালবাসার জন্মের পরও ভালবাসার দায়িত্ব মার ওপর। মা ভেবেছিলেন, সুহৃদের লালন পালনে বাবা যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, খাঁটি দুধের ব্যবস্থা, প্রতিদিন মুরগির বাচ্চার সুপের ব্যবস্থা, ভালবাসার জন্যও বাবা তাই করবেন। অবকাশে মা অত গৌণ নন এখন, সংসারের দায়িত্ব তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেলেও অন্য এক দায়িত্ব তাঁর আছে, নাতনি পালনের দায়িত্ব, সুতরাং সামান্য হলেও মর্যাদা তিনি পাবেন, এটি মা-ই কেবল ভেবেছিলেন। কিন্তু মাকে গৌণই করে রাখা হয়েছে অবকাশে, মাকে বাড়তি হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে আগের মত। বাবার কাছে ছেলের ছেলে যত মূল্যবান, মেয়ের মেয়ে তত মূল্যবান নয়। আর সংসারের কষর্নী হাসিনার কাছে তাঁর দুই সন্তান ছাড়া আর কারও কোনও সন্তানই মূল্যবান নয়, বরং চক্ষুশূল। স্বামী আর পুত্রবধূর অত্যাচার মাকে পীরবাড়ি নিয়ে যায় ঘন ঘন।
পীর বেশারাতুল্লাহ মারা যাবার পর তার পুত্র মুসা বনেছিলেন নতুন পীর। কিন্তু বেশিদিন পীর হওয়ার আনন্দ তিনি ভোগ করতে পারেন নি। হৃদপিণ্ডের অসুখে হঠাৎ মারা যান। এরপর পীর বেশারাতুল্লাহর নাতি, ফজলি খালার বড় ছেলে মোহাম্মদ হয়েছে পীর। এই মোহাম্মদই দিয়েছে ফতোয়া। এই ফতোয়া সমর্থন করেছে পীরবাড়ির সবাই। ফতোয়াঃ মা যেন পীরবাড়িতে আর না ঢোকেন।
মার অপরাধ? তসলিমা নাসরিন নাম্নী এক কাফেরকে জন্ম দিয়েছেন এবং এই কাফেরের সঙ্গে মার এখনও মা মেয়ে সম্পর্ক বজায় আছে।
এই মার অপরাধ। হয় আমাকে ত্যাগ করতে হবে, নয়ত পীরবাড়ি ত্যাগ করতে হবে। ফজলিখালাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে মা বলেছেন, ‘ফজলি, আমি আমার নিজের মেয়েরে ত্যাগ করবো কেমনে? একটা কি হয়?’
‘ত্যাগ তোমাকে করতেই হবে বড়বু। তোমার মেয়ে হল কাফের। কাফেরের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। যদি থাকে, তাহলে তুমিও কাফের।’
‘আমারে কাফের কইলি!’
‘এই দুনিয়ার ছেলে মেয়ে হিচ্ছে মিথ্যে মায়া। তোমাকে তো আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। ছেলে মেয়ের মায়ায় পড়ে তুমি যদি একটা কাফেরকে নিজের মেয়ে বলে স্বীকার কর, তাহলে বলে দিচ্ছি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। কোরানে আছে, তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে তো তোমাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করিব।’
‘নাসরিন মানুষের অনেক উপকার করে। ও খুব উদার। মেয়েদের ওপর অন্যায় অত্যাচার হয়, এইসবের বিরুদ্ধে লেখে। কত গরিব মেয়েরে ও টাকা পয়সা দিয়া সাহায্য করে। ও কি আল্লাহর ক্ষমা পাইব না?’
ফজলিখালা কঠিন গলায় বলেন, ‘না। কোনও ক্ষমা নাই তাদের। ও দোযখে যাবে। ও আল্লাহ বিশ্বাস করে না। বড়বু, তুমি খুব ভাল করেই জানো নাসরিন কোরান সম্পর্কে বাজে কথা লিখেছে। কোরান নাকি মানুষের লেখা। আমাদের নবীজি নাকি কামুক লোক। আল্লাহর নাকি অস্তিত্ব নাই। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লা।’
‘দেখ ফজলি, তর দুলাভাই আমারে কোনও টাকা পয়সা দেয় না। ময়মনসিংহ থেইকা কয়দিন পরপরই আমারে দূর দূর কইরা তাড়ায়। এহন নাসরিনের কাছে গিয়া যদি আমি না থাকতে পারি, আমি থাকব কোথায়?’
‘সেইটা আমি কি জানি! সোজা কথা, এই বাড়িতে আসতে চাইলে কোনও কাফেরের মুখ দেখা তোমার জন্য হারাম। আর কাফেরের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক যদি তুমি রাখতে চাও, তবে এই বাড়ি তোমার জন্য হারাম।’
মা কাঁদেন। মা ফুঁপিয়ে কাঁদেন। হাউমাউ করে কাঁদেন। ফজলিখালা মার কান্নার দিকে ফিরে তাকান না।
মাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় পীরবাড়ি থেকে। বলে দেওয়া হয়, মা যেন কখনও আর পীরবাড়ির ত্রিসীমানায় না ঘেঁসেন।
২৪. একথা সেকথা
ভালবাসাকে নিয়ে মা চলে এলেন ঢাকায়। ইয়াসমিন যেহেতু নটা পাঁচটা চাকরি করে, ভালবাসাকে মারই দেখাশোনা করতে হয়। ভালবাসার পুরো নাম স্রোতস্বিনী ভালবাসা। নামটি আমিই দিয়েছি। এই নাম নিয়ে প্রথম আপত্তি করেছিল মিলন।
এ কোনও নাম হল!
কখনও শুনিনি কারও নাম ভালবাসা।
তাতে কি!
লোকে হাসবে শুনে।
তাতে কি!
বড় হলে ছেলেরা টিটকিরি দেবে।
তাতে কি!
মিলনের মা মোসাম্মৎ আফিফা খাতুন নামটি ঠিক করেছিলেন। ওই নামটিই মেয়ের জন্য রাখা প্রায় হচ্ছিল হচ্ছিল, কিন্তু ইয়াসমিনের জোর আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। ইয়াসমিন আমার দেওয়া নামটির পক্ষে রীতিমত আন্দোলন করে এটিকেই বহাল রাখে। এখন গাল ভরে সবাই ফোলা ফোলা গালের মেয়েটিকে ভালবাসা বলে ডাকে। ভালবাসা গুটি গুটি পায়ে হেঁটে বেড়ায় সারা বাড়িতে। দেখে আমার খুব ভাল লাগে। আমার কোলে বসে মাঝে মাঝে কমপিউটারের কীবোর্ড টিপে আমার লেখা নষ্ট করে দেয়, এতেও আমার রাগ হয় না। ভালবাসার জন্য ভালবাসা জাগে।
মার যাযাবর জীবন যে শান্তিনগরের বাড়িটিতে স্থিরতা পাবে, তা পায় না। মা স্থিরতা চান, কিন্তু তাঁকে দেবে কে? অবকাশে বাবার অধীনতা মানতে হয়। আর শান্তিনগরে মানতে হয় আমার অধীনতা। মার পরাধীন জীবন পরাধীনই থেকে যায়। নাহিদকে মার পছন্দ নয়। নাহিদ নিজে সিগারেট খায়, আমাকেও সিগারেট খাওয়া শেখাচ্ছে, এটি তো আছেই, তার ওপর মার ধারনা নাহিদ খুব বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু নয় আমার। মাকে আমি ধমকে চুপ করতে বলি, বলে দিই আর যেন একটি কথা না উচ্চারণ হয় নাহিদের বিরুদ্ধে। মা আড়ালে গিয়ে চোখের জল ফেলেন। নাহিদ আমার বাড়িতে যখন খুশি আসবে, তাকে যেন সম্মান করা হয়, এটি জানিয়ে দিই। সম্মান নাহিদকে ঠিকই করা হচ্ছিল, কিন্তু নাহিদ অবশ্য আমাকে ফাঁক পেলেই বলে আমার বাড়ির কোন মানুষটি তার সঙ্গে কোন সৌজন্যটি দেখায়নি, দরজা খুলতে দেরি করেছে, সময়মত খাবার দেয়নি, তার দিকে অবজ্ঞা চোখে চেয়েছে। নাহিদের এসব শুনে সব রাগ আমার গিয়ে পড়ত মার ওপর। কিন্তু একদিন নাহিদের ওপর আমার নিজেরই রাগ হয়। নিপার মা নিপাকে নিয়ে আমার বাড়িতে নাহিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছিলেন এক রাতে। আমার বাড়িতে নাহিদের সঙ্গে নিপার দেখা হতে হতে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। মাঝে মাঝে নাহিদ রাত কাটায় নিপাদের বাড়িতে। শেষ রাতটিতেই ঘটনাটি ঘটেছে, নিপার সঙ্গে রাতে এক বিছানায় শুয়েছিল নাহিদ, কিন্তু নাহিদের হাত অন্ধকারে বারবারই নিপার শরীরে আনাচে কানাচে গিয়েছে,একসময় সে জোরও করেছে নিপার কাপড় জামা খুলে নিতে। নিপা তার মাকে এই ঘটনা জানিয়ে দিলে নিপার মা নিজে আসেন আমাকে বলতে যে আমি যেন নাহিদকে বলে দিই আর কোনওদিন যেন সে নিপাদের বাড়িতে না ঢোকে। এটি কোনও কারণ নয় নাহিদকে সন্দেহ করার বা তার ওপর রাগ করার। নাহিদ সম্ভবত সমকামী, যা আমার আগে জানা ছিল না। নাহিদ জানায়নি, সেটি সে লুকিয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত ব্যপার সে লুকোতেই পারে, এ তার দোষ নয়। সন্দেহটি জাগে যখন একটি পত্রিকায় কায়সারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে লেখা হয়। লেখা হতেই পারে, কায়সারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক মোটেও লুকোনো কোনও ব্যপার নয়। কিন্তু কায়সার আমার হাতে একদিন মার খেয়েছিল, মার খেয়ে ছেঁড়া শার্ট পরেই তাকে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল এ কথাটি লেখা হয়েছে। ঠিক এরকম না হলেও কাছাকাছি একটি ঘটনা ঘটেছিল এবং নাহিদ সেটি দেখেছে। বাড়িতে তখন আর কেউ ছিল না যে কি না পত্রিকার কাউকে এ খবরটি দিতে পারে। সেই থেকে নাহিদের ওপর যে আমার আস্থা ছিল, সেটি কমে যায়। আমি আর দরজা খুলি না নাহিদ এলে। সে খুব চেষ্টা করে আমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করার,অনুরোধ আবদার, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা, চিঠি লেখা, ফোন, সবই সে করে। কিন্তু আমাকে সে কিছুতেই নরম করতে পারে না। আমার ব্যক্তিগত ব্যপার নিয়ে পত্রিকায় লেখা ছাপা হতেই পারে। প্রতিদিনই ছাপা হচ্ছে। এসব আমি এখন আর গ্রাহ্য করি না। কারণ একটি সত্য ঘটনার সঙ্গে সাতটি বানানো ঘটনা মিশিয়েই সাধারণত আমার ব্যক্তিগত জীবন রচনা করে হলুদ সাংবাদিকরা। প্রথম প্রথম আমার দুঃখ হত, রাগ হত। কিছু না হলেও ভাবনা হত। এখন ওসব গল্পে একবার চোখ বুলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই। নাহিদকে আমি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু গুপ্তচর হিসেবে আমার কাছে সে আসুক, তা আমি চাই না। নাহিদ নিজে আমার সম্পর্কে লিখতে পারে বা আমার সম্পর্কে বলতে পারে অন্য কোনও সাংবাদিককে, এতে আমার আপত্তি নেই। সমালোচনা থাকতেই পারে। কিন্তু লুকিয়ে কেন! যা সে আমার কাছে বলছে, আমার আড়ালে গিয়েই সে সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলছে, তা যখন জানা হয়ে যায়, তখন সে আমার আর যা কিছুই হোক, বন্ধু নয়, এ ব্যপারে আমি নিশ্চিত। সামনে এক কথা, আড়ালে আরেক কথা বলার চরিত্র অনেক লোকের। এমন চরিত্র আমার মোটেও পছন্দ নয়, এমন চরিত্রের মানুষকে আমার বাড়িতে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ আমি দিতে চাই না।
গৌরী রাণী দাসকে যখন আমার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম, মা বলেছিলেন, ‘অজানা অচেনা কাউরে বাড়িতে জায়গা দিবি! এইটা কি ঠিক হবে!’ মাকে আমি এক ধমক দিয়ে থামিয়েছিলাম, বলে, যে, ‘আমার বাড়িতে আমি কারে জাগা দিব না দিব সেইটা তোমার ভাবতে হবে না। এইটা আমার বাড়ি।’ আমার কণ্ঠস্বর আমার কাছেই খুব বাবার কণ্ঠস্বরের মত ঠেকেছিল। বাবার এরকম দিনে দুবার করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে অবকাশ নামের বাড়িটি তাঁর বাড়ি।
গৌরী রাণী দাস গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল, তার পক্ষে এবং দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তির দাবি করে আমি একটি কলাম লিখেছিলাম পত্রিকায়। আমার কথা কোনও না কোনও ভাবে কানে যায় গৌরী রাণীর। কানে যাওয়ার পরই গৌরী আমার বাড়িতে এসে আশ্রয় চায়। ধর্ষকদের বিরুদ্ধে সে মামলা করেছে, মামলার কারণে তাকে থাকতেই হবে ঢাকায়, কিন্তু এ শহরে কোনও থাকার জায়গা নেই তার। আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি একটি অসহায় মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়া। গৌরী রাণীকে বলেছি, যতদিন তার দরকার, সে নিশ্চিন্তে আমার বাড়িতে থাকবে, খাবে। মামলায় টাকা পয়সা দরকার হলেও আমার কাছ থেকেই নেবে। গৌরী রাণীকে বাড়িতে রীতিমত রানীর আসনে বসিয়ে দিলাম। সপ্তাহ দুই পার হলে মা বললেন, গন্ধে বাড়িটায় টিকা যায় না। মার ধারনা গন্ধটি গৌরীর গায়ের। মাকে তখনও হিংসুটে সংকীর্ণ মনা বলে থামিয়েছিলাম। পরে একদিন নিজেই আমি বোটকা গন্ধ পাই গৌরীর গা থেকে বেরোচ্ছে। গৌরী গোসল করে এলেও ওর গা থেকে যায় না। গৌরী এ বাড়িতে আসার পর থেকেই গন্ধটি আমি পাচ্ছিলাম, কিন্তু কখনও মনে হয়নি এ গৌরীর গন্ধ। গন্ধ দিন দিন তীব্র হয়ে উঠল। আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না গৌরীকে এ বাড়িতে চলে যেতে বলার। আমি বরং ওর কাপড় চোপড় ধোবার ব্যবস্থা করি। নাক ঢেকে মিনু গৌরীর কাপড়জামা ধুয়ে দেয়। তার পরও গন্ধ যায় না। গন্ধটি গেল, গৌরী যেদিন গেল।
মহাভোজের আয়োজন কর, আমার লেখক বন্ধুরা খাবেন।
রাঁধাবাড়া শেষ। কিন্তু এক্ষুনি আবার সাতজনের জন্য রাঁধো। সাতজন গার্মেণ্টেসএর মেয়ে আসছে খেতে।
ঘর ছেড়ে দাও, কলকাতা থেকে দাদা বা দিদি আসছেন। পাঁচদিন থাকবেন।
মদ আনাতে হবে, কবি বন্ধুরা পান করবেন।
জোরে গান বাজবে, যত জোরে ইচ্ছে করে, আমার পরান যেমন জোরে চায়।
কেউ শব্দ কোরো না, আমার লেখার অসুবিধে হয়।
রাত দুটো পর্যন্ত আড্ডা চলছে, তাতে কার কি! এটা আমার বাড়ি, সারারাত আড্ডা দেব। ড্রাইভারকে খাবার দাও, রান্নাঘরে না, ডাইনিং টেবিলে।
এসব কোনও কিছুতে মার আপত্তি নেই। দিন দুপুরে কায়সারকে নিয়ে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করছি, ঘন্টা পার করে দুজনই এলো চুলে বেরোচ্ছি ঘর থেকে, এতেও মার আপত্তি নেই। কিন্তু তারপরও দেখি মা হঠাৎ হঠাৎ আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যান। মা বাড়িতে থাকলে বাড়িটিকে বাড়ি মনে হয়। কোথাও কোনও ধুলো নেই। স্নানঘরের মেঝেয় জল পড়ে নেই। বিছানার চাদর কুঁচকে নেই। কাপড় চোপড় আধোয়া নেই। ক্ষিধে পাওয়ার আগেই খাবার দেওয়া হয় টেবিলে। যা যা ভালবাসি খেতে তাই দেখি রান্না হচ্ছে। লেখার টেবিলে ঘন ঘন চা দিতে কাউকে বলতে হয় না। বলার আগেই চা এসে যায়। বাড়ির সব কিছু আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ওঠে। মা থাকলে বুঝি না যে মা আছেন। মা না থাকলেই টের পাই যে মা নেই। ইয়াসমিনকে একদিন মার কথা জিজ্ঞেস করলে বলে, মা রাগ কইরা চইলা গেছে।
‘কেন রাগ করছে?’
‘তুমি নাকি বলছিলা, টাকা পয়সা বেশি খরচ হইতাছে বাজারে।’
‘হ তা কইছিলাম। কিন্তু মারে উদ্দেশ্য কইরা তো কই নাই।’
‘মা ভাবছে মারে কইছ।’
মা আমার স্বাধীনতায় কোনও বাধ সাধেন না। কেবল তাঁর প্রতি আমার দুর্ব্যবহার তাঁকে কাঁদায়। তাঁকে যাযাবর করে। মা এখানে আমার কাছে ধমক খেয়ে অভিমান করে অবকাশে আশ্রয় নেন। অবকাশে বাবার ধমক খেয়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসেন। মার স্থায়ী কোনও জায়গা নেই বসবাসের। মার নিজস্ব কোনও ঘর নেই। সংসার নেই। আমি লক্ষ করি না, মার প্রতি ব্যবহারের বেলায় আমি আমার অজান্তেই বাবা হয়ে উঠি। বাবার প্রতি আমার সমীহ বরাবরই ছিল, আছে, যতই তিনি নিষ্ঠুর হন না কেন। তাঁকে নিষ্ঠুর বলে গাল দিয়েছি, কিন্তু তাঁর প্রতাপের প্রতি গোপনে গোপনে শ্রদ্ধা ছিল বোধহয়, যা কখনও বুঝিনি যে ছিল। তাই যখনই আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, যখনই স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে জীবনে, তখনই আমার অজান্তেই আমি ছোটখাটো বাবা হয়ে উঠি। প্রতাপশালী। ক্ষমতাবান। মার দারিদ্র, মার হত ভাগ্য, মার রূপ হীনতা, মার হীনমন্যতা, মার নুয়ে থাকা, মার কষ্ট, মার নির্বুদ্ধিতা, মার বোকামো, মার ধর্মপরায়ণতা, মার কুসংস্কার কোনওদিন আমাকে আকর্ষণ করেনি। এসব আমাকে মা থেকে কেবল দূরেই সরিয়েছে। মা আমার সংসারে নিজেকে প্রয়োজনীয় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যান। আমার তবুও মাকে বাড়তি মানুষ বলে হয়। বাবার যেমন মাকে মনে হয়, অবকাশে। ঈদ পরব এলে আমি বাবার জন্য নানারকম উপহার নিয়ে ময়মনসিংহে যাই। মার কথা আমার মনে থাকে না। যদি কখনও দিতে হয় কিছু মাকে, আলমারি খুলে আমার পুরোনো কোনও শাড়ি, যা অনেকদিন পরেছি, এখন আর ভাল লাগে না পরতে, তাই দিই। তা পেয়েই মার খুশির অন্ত নেই। প্রথম নিতে চান না। বলেন, ‘তুমি পছন্দ কইরা কিনছ শাড়ি, তুমি পড়। আমার যা আছে, তা দিয়া ত চলতাছেই।’
‘না এই শাড়ি আমি ত আর পরি না।’
‘তারপরও কখনও যদি ইচ্ছা হয়, পরতে পারবা।’
‘না। না। এই শাড়ি এখন আমার আর পছন্দ না।’
মা অগত্যা নেন। সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলেন, ‘নাসরিনের পছন্দের একটা শাড়ি নাসরিন দিয়া দিল আমারে। শাড়িটা একদিনও ও পরে নাই।’
খরচ বাঁচানোর জন্য মাকে যদিও কোনওদিন আমি বলিনি, মা তবু আমার সংসারের খরচ বাঁচাতে চেষ্টা করেন। এক মুরগি একদিনের জন্য কেনা হল, তা দিয়ে দুদিন চালাতে চান। ভাগে কম পড়লে রাগ করি। তিনি নিজের ভাগেরটুকুও আমার পাতে তুলে দিয়ে কাজের মেয়েদের সঙ্গে বসে ডাল ভাত খেয়ে ওঠেন। আমার আর্থিক অবস্থা নিয়ে আমার চেয়ে মার দুর্ভাবনা বেশি। ভালবাসা হাঁটতে গেলে মার ভয়, পড়ে যাবে বুঝি। আমি বারান্দায় দাঁড়ালে মার ভয় কোনও ঘাতক বুঝি আমাকে দেখছে রাস্তা থেকে অথবা আশে পাশের কোনও বাড়ি থেকে। মার ভয় দেখতে বড় বিচ্ছিরি লাগে আমার। আগের মত এখন আর পুলিশ পাহারা নেই। দরজার পুলিশ হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেছে। মিছিল যখন শান্তিনগরের দিকে আসে, তখনই কেবল আমার বাড়ির সামনের রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আমি সময় অসময়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ি, মা পেছন থেকে বলেন, ‘বাইরে যাইস না। কখন কি হয়, কে জানে।’
আমি পেছন ফিরি না। মা বলতে থাকেন, ‘যাইতে হইলে কাউরে নিয়া যা। একলা যাইস না।’
আমি তবুও পেছন ফিরি না।
বুকের মধ্যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভয় পুষে রাখতে রাখতে আমার এখন অসহ্য লাগে। কিন্তু এই যে বেরিয়ে যাই, যাই কোথায়? যাই শহর ছাড়িয়ে কোথাও। অতি বিনয়ী, অতি স্বল্পভাষী, অতি সৎ সাহাবুদ্দিন জিজ্ঞেস করেন, ‘আপা কোনদিকে যাবো?’ ‘যান, যেইদিকে খুশি যান।’
আমার কোনও ঠিকানা নেই যাওয়ার। সাহাবুদ্দিন যেতে থাকেন দক্ষিণের দিকে। দক্ষিণের দিকে কোনও গন্তব্য নেই। শহর ছাড়িয়ে নির্জনতার দিকে, গ্রামের দিকে, বনের দিকে, নদীর দিকে। আমার ভাল লাগে এই গতি, এই ছুটে যাওয়া। জানালায় হাওয়া এসে চুল এলো করে দেয়, ভাল লাগে। ইচ্ছে করে বনের পথে একা একা হেঁটে যাই, কোনও কলাপাতার বেড়ার আড়ালে গ্রামের কোনও মাটির ঘরে যাই, পুকুরে স্নান করি, নদীতে সাঁতার কাটি, বিলে নেমে মাছ ধরি, গ্রামের ফ্রক পরা মেয়েদের সঙ্গে গোল্লাছুট খেলি। ইচ্ছেগুলোকে আমি দমন করি, আমি জানি আমার শহুরে ঢংএ শাড়ি পরা, আমার গাড়ি, আমার জুতো-পা, আমার ছোট চুল সবই উদ্ভট দেখাবে এ অঞ্চলে, সকলে সার্কাসের ক্লাউন দেখছে এমন চোখে আমাকে দেখবে। গাড়ি থামিয়ে সেদিন গাড়িতেই বসে থাকি। সাহাবুদ্দিনের ঘর বাড়ি বউ বাচ্চার কথা জিজ্ঞেস করি। সাহাবুদ্দিন সংকোচে সলাজে উত্তর দেন। যে টাকা তিনি মাইনে পান, তা দিয়ে সংসার চলে কি না জিজ্ঞেস করলে বলেন, চলে। কোনও অভাব নেই? না। অন্য ড্রাইভার দেড় দুহাজার মত পায়, সাহাবুদ্দিনকে আমি দিই মাসে আড়াই হাজার। ইচ্ছে করেই দিই, এই টাকা সাহাবুদ্দিন দাবি করেননি। দুপুরে আমার বাড়িতেই খান। যদিও দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তাঁর চাকরির সময়, কিন্তু মাসে বেশির ভাগ দিনই তাঁকে আটটা নটা পর্যন্ত থাকতে হয়। কখনও কখনও রাত দুটো। কোনওদিন আপত্তি করেননি, যে, এত রাত পর্যন্ত থাকা সম্ভব নয়। বাড়তি সময়ের জন্য তাকে কিছু বাড়তি টাকা দিতে যাই, সে টাকা হাতে নিতে সাহাবুদ্দিন লজ্জায় মরে যান। জোর করে দিতে হয়। সব মিলিয়ে মাসে তাঁর তিন হাজার টাকার মত সম্ভবত হয়। সাহাবুদ্দিনের আগে একটি ড্রাইভার ছিল, অল্প বয়স ছিল সেই ড্রাইভারের, ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাত, আর কোথাও কাউকে তুলে আনতে পাঠালে পথে নেমে তেল বিক্রি করত গাড়ির। ওই ছোকরা ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে সাহাবুদ্দিনকে চাকরি দেওয়ার পর আমার কখনও ভাবতে হয় না গাড়ির ব্যপারে। গাড়ি মুছে পরিস্কার করে ঝকঝকে করে রাখেন সাহাবুদ্দিন। ইস্টার্ন হাউজিংএর গ্যারেজএ গাড়ি রেখে ড্রাইভাররা আড্ডা পেটায়, তাস খেলে। সাহাবুদ্দিনকে ওই আড্ডায় কখনও দেখিনি। তিনি গাড়ির ভেতর বসে বসে নামাজ শিক্ষা জাতীয় পকেট বই পড়েন। একবার তিনি সভয়ে জানিয়েছিলেন, কিছু অচেনা লোক তাঁকে প্রতিদিন খুঁজতে আসে গ্যারেজে। সাহাবুদ্দিনের ভয় ওই অচেনা লোকগুলো আমার কোনও ক্ষতি করার উদ্দেশে আসে তাঁর কাছে। সাহাবুদ্দিনকে শাসিয়ে যেতে আসে, যেন আমার গাড়ি আর না চালায় বা গাড়ির ভেতর গোপনে বোমা রাখতে আসে। সাহাবুদ্দিন তাই নিজেই গাড়ি থেকে বের হন না, প্রহরীদের বলে দিয়েছেন যেহেতু ওই লোকগুলো তাঁর চেনা কেউ নয়, যেন ওদের গ্যারেজের দিকে যাওয়ার সুযোগ না দেওয়া হয়। সাহাবুদ্দিন, পাজামা পাঞ্জাবি পরা লিকলিকে ক্লিন সেভড পঁয়ষট্টি বছর, আমাকে রক্ষা করেন আমাকে না জানিয়ে। তাঁকে কোনওদিন বলিনি কি হচ্ছে দেশে আমাকে নিয়ে। তিনি খবর পান কি হচ্ছে। তিনি যে জানেন তা আমাকে জানতে দেন না। শহরের রাস্তায় আমার গাড়ির দিকে কোনও লোক বা কোনও দল এগোতে থাকলে তিনি দ্রুত গাড়ি চালান, আমাকে বলতে হয় না দ্রুত পার হয়ে যেতে। আমাকে বলতে হয় না যে রাস্তায় মিছিল বা সভা হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে সেদিকে না যেতে। তিনি নিজেই অন্য রাস্তা ধরেন। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, ঘুরে যাচ্ছেন কেন?
বললেন, ‘ওদিকে আজকে মিছিল আছে।’
‘কিসের মিছিল?’
সাহাবুদ্দিন চুপ। তিনি জানেন না যে আমি জানি কিসের মিছিল হচ্ছে।
‘কারা মিছিল করছে?’
‘ওরা ভাল লোক না।’
সাহাবুদ্দিনের সংক্ষিপ্ত উত্তর। ওদিকে ভাল লোকের মিছিল হচ্ছে না, ওদিকে আমার যাবার দরকার নেই।
‘গাড়িতে তেল লাগবে?’
‘না।’
গাড়ির তেল ধীরে খরচ হয়। যেটুকু চলে গাড়ি, সেটুকুই খরচ।
‘সাহাবুদ্দিন, আপনার টাকার দরকার আছে? টাকা লাগবে কিছু?’
‘না।’
‘আপনার ছেলে বলেছিলেন মেট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে। যদি কখনও দরকার হয় কিছু বলবেন।’
‘আমার লাগবে না।’
সাহাবুদ্দিন বড় অপ্রতিভ বোধ করেন টাকা পয়সার প্রসঙ্গ উঠলে। নম্রতা আর নির্লোভতার একটা সীমা আছে, সাহাবুদ্দিন সীমা ছাড়িয়ে যান। মাঝে মাঝে মনে হয় সাহাবুদ্দিন এই গ্রহের কেউ নয়, অন্য গ্রহ থেকে অন্যরকম একজন মানুষ এই নোংরা পৃথিবীতে এসে পড়েছেন। ভাবি, আজ যদি দেশের মানুষগুলো সাহাবুদ্দিনের মত সৎ হত, তাহলে হয়ত দেশটির চেহারা বদলে যেতে পারত। হাতে গোনা কিছু ধনী লোক কোটি কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বসে আছে, কোনওদিনই তা আর ফেরত দিচ্ছে না। সরকারের সঙ্গে বেশ খাতির তাদের, সরকার ঋণখেলাপিদের গোপনে ক্ষমা করে দেয়। যে সরকারই আসে, সে সরকারের সঙ্গেই এদের খাতিরের ব্যবস্থা আছে। সততা কোথায় আছে আর? শিক্ষকদের সৎ বলে জানতাম। শিক্ষকদের মধ্যেও অসততার বীজ রোপন করা হয়ে গেছে। তাঁরাও আজকাল মোটা টিউশন ফি নিয়ে ছাত্র পড়িয়ে পরীক্ষা পাশের নিশ্চয়তা দেন। পুলিশ ঘুষ খাচ্ছে। কৌশলী খাচ্ছে, প্রকৌশলী খাচ্ছে। রাস্তাঘাট আজ নির্মাণ হল, তো কাল ভেঙে যাচ্ছে। ভেজাল সবখানে। ডাক্তাররা হাসপাতালের রোগীকে প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে টাকা আদায় করে অপারেশন করছে, অপারেশনের প্রয়োজন না থাকলেও পেট কাটছে টাকার জন্য। মন্ত্রী ঘুষ খাচ্ছে, আমলারা খাচ্ছে। যাদের খাবার আছে, তারাই আরও বেশি করে খেতে চাইছে। আর যাদের নেই, যারা খেতে পাচ্ছে না, তারা মুখ বুজে অন্যের খাওয়া দেখছে। সততা যদি টিকে থাকে কোথাও, দরিদ্রদের মধ্যেই আছে। কিন্তু মুখ বুজে আছে কেন সবাই! কেন নিজের অধিকারটুকুর দাবি তারা করে না। রিক্সাঅলারা রোদে জলে ভিজে অমানুষিক পরিশ্রম করে সামান্য কটি টাকা রোজগার করে, আরোহীদের মার খায় ধমক খায় কিন্তু প্রতিবাদ করে না। পাঁচতারা হোটেলের কিনারে, বারিধারার বড় বড় প্রাসাদের পাশে নোংরা বস্তিতে জীবন যাপন করছে মানুষ অথচ প্রতিবাদ করছে না। ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকেরা দেখছে বড় বড় রেস্তোরাঁয় লোকেরা পেট পুরে খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছে, দেখেও কেড়ে খেতে চাইছে না কোনও খাবার। একবার কাউরান বাজারে গিয়েছিলাম রাতে, ওখানে অনেক রাতে ট্রাক ভরে শাক সবজি আসে, ট্রাক থেকে শ্রমিকেরা নামায় সেসব, কিছু সবজি কিনে ফিরে আসার সময় দেখেছিলাম, শহরের শ্রমিকেরা ফুটপাতে ঘুমোচ্ছে, কারও কোনও ঘর নেই, ঘুমোবার জায়গা নেই, গরমে কোনও হাওয়া নেই, মশা কামড়াচ্ছে, কোনও মশারি নেই, সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত, রাস্তার কিনারে কোথাও একটু ঘুমোবার জায়গা পেলেই খুশি ওরা, ওরাও প্রতিবাদ করতে জানে না। ধনী আর দরিদ্রের প্রকট বৈষম্য দেখে আমার বড় রাগ হয়। নিজের কথা ভাবি, রাগ করার কী অধিকার আছে আমার! আমিই বা ধনীদের চেয়ে আলাদা কোথায়, আমাকে ধনী বলেই বিচার করবে যে কোনও উদ্বাস্তু উন্মুল মানুষ। আমি একটি দামি আ্যপার্টমেন্ট কিনেছি, আমার একটি গাড়ি আছে। আমি ধনীই বটে। নিজেকে আমি সান্ত্বনা নিই এই বলে যে আমি কোনও অসততা করে টাকা উপার্জন করিনি, আমি কোনও অবৈধ ব্যবসা করি না, লোক ঠকাই না, একটিও কালো টাকা আমার নেই। তারপরও একটি গ্লানি আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। আমি কি এখন সব ছেড়ে ছুড়ে ফুটপাতে রাত কাটাবো, বস্তিতে ঘর তুলব? আমি কি সব টাকা পয়সা বিলিয়ে দিয়ে না খেয়ে বা আধ পেট দিন কাটবো? এতে কি ধনী দরিদ্রের বৈষম্য শেষ হবে? হবে না। আমি কি লিখে এই বৈষম্য দূর করতে পারব? আমি জানি, পারব না। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে দূর্নীতি। কোনও রাজনৈতিক নেতাই দরিদ্র মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের কথা ভাবে না। চেষ্টা করে না। গণতন্ত্র ব্যবহার করে যে দলই ক্ষমতায় আসে, ক্ষমতায় এসে ক্ষমতা অপব্যবহার করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়াই আসল উদ্দেশ্য। দেশ এবং দেশের মানুষের মঙ্গল, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করার নীতি কারওরই নেই। একবার বারিধারার বস্তির এক হতদরিদ্র লোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, চোখের সামনে এত যে ধনী দেখছেন, এত যে ওদের ধন দেখছেন, কি রকম লাগে আপনাদের? আপনারাও মানুষ, ওরাও মানুষ, কিন্তু ওরা সুখে থাকবে, আপনারা কষ্টে থাকবেন, এই নিয়মটি কেন মেনে নিচ্ছেন? কেন ধনীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন না? লোকটি বলেছিল, ‘আল্লায় তাদেরে দিছেন, আমাদেরে দেয় নাই। ইহলোকে যদি কষ্ট করি, পরলোকে আল্লাহ অনেক দিবেন। এই সময় ঈমান মজবুত রাখা জরুরি। আল্লাহ তো আমাদেরে দুর্দশা দিয়া আমাদের ঈমান পরীক্ষা করতেছেন। ঈমান যদি ঠিক রাখতে পারি, তাইলে আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।’ আমি নিশ্চিত, লোকটি নিজের বুদ্ধি থেকে এই কথা বলেনি। বলেছে সেই কথা যা তাকে শিখিয়েছে আমাদের নেতারা। আমাদের রাজনীতিকরা ধর্মকে ব্যবহার করেন গরিবদের দাবিয়ে রাখার জন্য। তা না হলে আজ বারো কোটি লোকের মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করা আশি ভাগ লোক যদি প্রতিবাদ করত, যদি পথে নামত, তবে ধনীর সাধ্য ছিল না আরাম আয়েশে জীবন যাপন করা। ধর্ম তাই ধনীদের আরামে রাখার একটি অস্ত্র। ধর্ম রাজনীতিকদেরও অস্ত্র। ধর্মের কথা বলে গরিবকে নিশ্চুপ রাখা যায়, ধর্মের কথা বলে ভোটে জেতা যায়। ধর্মের কথা বলে ধর্মীয় অনুভূতি উসকে দেওয়া যায়। ধর্মের কথা বলে উড়ির চড়ের ঘুর্ণিঝড়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুকে আড়াল করা যায়, হাজার হাজার ঘরহীন মানুষকে আকাশের তলে বাস করানো যায়। প্রতিবছর বন্যায় ঘরবাড়ি ভাঙা, জলে তলিয়ে যাওয়া সহায় সম্বলহীন মানুষকে বলা যায় আল্লাহ ঈমান পরীক্ষা করছেন। ঈমানের পরীক্ষা কেবল গরিবদেরই ওপরই কেবল? এই প্রশ্নটি করারও কারও সাহস নেই। এতে লাভ সকল বিত্তবান এবং মধ্যবিত্তর। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন বিত্তবান হওয়া। বিত্তবানদের সব পন্থাই তারা অবলম্বন করে। অথচ কোনও সামাজিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে যে আন্দোলনই গড়ে ওঠে, কিছু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সচেতন মানুষ দ্বারাই তা গড়ে ওঠে। তাই আন্দোলন কখনও খুব শক্ত হয়ে দানা বাঁধে না। থেমে থেমে যায়। এর পেছনে যে কারণটি আছে, তা নিশ্চয়ই, যেহেতু মধ্যবিত্তদের দলটি, সমাজ সচেতন হলেও, সমাজের মঙ্গলের জন্য আন্দোলন করলেও, সত্যিকার ভুক্তভোগী নয়।
ভুক্তভোগীরা যখন আন্দোলনে নামে, জীবন দিয়ে নামে। কিন্তু ভুক্তভোগীদের আন্দোলন মাটি করে দেওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটছে। দেশের কোনও কারখানায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক আইন মেনে চলা হয় না। শ্রমিকদের খাটানো হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি, মাইনে দেওয়া হচ্ছে কম, তার ওপর সুযোগ সুবিধে যা তাদের প্রাপ্য তার কিছুই দেওয়া হচ্ছে না। এসবের বিরুদ্ধে কোনও কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন করতে চাইছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক নেতাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে মালিকের পক্ষ থেকে দিয়ে দেওয়া হল মোটা অংকের টাকা। ব্যস, নেতা থামিয়ে দিল আন্দোলন। এভাবেই চলছে দেশ। সেই কত কাল আগে লাঙল ব্যবহার শুরু। কৃষি ব্যবস্থার কত উন্নতি হয়ে গেল কত দেশে, আর কৃষি-প্রধান দেশটিতে এখনও লাঙলই সম্বল জমি চাষ করার জন্য। যে কৃষকরা ফসল ফলাচ্ছে, সেই কৃষকদের হাতে ফসলের সঠিক মূল্য পৌঁছোচ্ছে না। কৃষক এবং ক্রেতার মাঝখানের ব্যবসায়ীরাই মূল্যের অধিকটা পকেটে পুরছে। এমন একটি ব্যবস্থা কি কখনও করা সম্ভব নয় যে ব্যবস্থায় ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে এই বিশাল পার্থক্যটি ঘুচবে! যখন ধনী অত বেশি ধন তৈরি করার সুযোগ পাবে না, আর দরিদ্রকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হবে না! কজন মানুষ সৎ পথে ধনী হতে পারে এ দেশে! খুব কম। যারা খুব ধনী, বেশির ভাগই অসৎ পথে ধনী হয়েছে, অন্যকে ঠকিয়ে ধন বানিয়েছে নিজের জন্য। উপার্জনের কর ফাঁকি দিয়ে চলছে অধিকাংশ ধনী। ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য ঘোচানোর ব্যবস্থাটি তৈরি করে মানুষের মধ্যে সমতা আনতে যে সততা আর নিষ্ঠা প্রয়োজন তা কজন মানুষের মধ্যে আছে! মানুষ নিজের কথাই ভাববে নাকি অন্যের! মানুষ যদিও সৎও হয়, সরকারের অসততার কারণে মানুষ অসৎ হতে বাধ্য হয়। ওপরতলায় দূর্নীতি বাড়লে নিচ তলাতেও দূর্নীতি বাড়ে। দেশটি দরিদ্র দেশ। দেশটির মাটির তলে এমন কিছু সম্পদ নেই যা দিয়ে রাতারাতি ধনী হয়ে যেতে পারে। জনসংখ্যা উন্মাদের মত বাড়ছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বছর বছর মানুষ মরছে, বাস ট্রাক গাড়ি রেলগাড়ি যখন তখন উল্টো হয়ে পড়ছে, জাহাজ ডুবছে, লঞ্চ ডুবছে —একসঙ্গে তিনশ চারশ মানুষ এক মিনিটেই মরে যাচ্ছে। এত মরেও জনসংখ্যা রোধ হচ্ছে না। বাড়ছেই। অসুখে অপুষ্টিতে শিশু মরছে, শিশুর মৃত্যু হার বাড়লে শিশুর জন্মের হারও বাড়ে। অনিশ্চয়তা থেকে বাড়ে। চারদিকে অশিক্ষা বাড়ছে। কুশিক্ষা বাড়ছে। অভাব বাড়ছে। অন্ধত্ব বাড়ছে। সংশয় বাড়ছে, হতাশা বাড়ছে। হতাশা বাড়লে ধর্ম বাড়ে। দিনে কয়েকটি করে খোদ ঢাকা শহরেই ইসলামি জলসার আসর বসে। ধর্ম এখন বেশ বড় একটি ব্যবসা। ধর্মের ব্যবসা যাদের আছে, তারা ভাল কামাচ্ছে। লোক ঠকানোর ব্যবসা যারাই করে, ভাল কামায়। যত বেশি লোক ঠকাতে পারবে, তত বেশি কামাই। দেশে একজনও সৎ নেতা বা নেত্রী নেই, যার ওপর ভরসা করা যায়। কোনও নেতাই দেশ এবং দেশের মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবে না। সবাই আছে নিজের স্বার্থ নিয়ে। ডঃ কামাল হোসেন গণফোরাম নামে একটি রাজনৈতিক দল শুরু করেছেন। তিনি একসময় শেখ মুজিবর রহমানের খুব প্রিয় লোক ছিলেন। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানটি তাঁরই লেখা। মুজিব আমলে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হওয়ায় তিনি আওয়ামি লীগ থেকে বেরিয়ে আসেন। গণফোরামের সদস্য সংখ্যা খুবই কম, বেশির ভাগ সদস্যই উচ্চজ্ঞশক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, আইনজ্ঞ। এই দলে বেশ কজন অভিজ্ঞ বাম রাজনীতির নেতা আছেন। কোনওদিন যদি ক্ষমতায় যেতে পারে গণফোরাম, তবে আমার বিশ্বাস দেশটির চেহারা পাল্টাবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ডঃ কামাল হোসেন এই গণফোরামকে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করতে পারছেন না। সম্ভবও নয়। জনপ্রিয় রাজনীতি করতে হলে কর্মী পুষতে হয়, সন্ত্রাসী পুষতে হয়, জনগনকে ধোঁকা দিতে হয়। সেটা আদর্শের রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত, তাঁরা পারেন না।গত নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে হেরে গেছেন অশিক্ষিত ট্রাক ব্যবসায়ী হারুন মোল্লার কাছে। কামাল হোসেন একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ, জাতিসংঘের উপদেষ্টা, শিক্ষিত, সৎ, সেকুলার, অথচ তাঁকে হেরে যেতে হয় রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ একটি লোকের কাছে। কি নাম এই দেশের গণতন্ত্রের যে গণতন্ত্রের ভোট টাকা দিয়ে কেনা হয়? এ আর যাই হোক সত্যিকার গণতন্ত্র নয়। দেশের আশিভাগ দরিদ্রর কাছ থেকে ভোট পাওয়ার জন্য তাকে মিথ্যে আশ্বাস দাও, কিছু টাকা হাতে ধরিয়ে দাও, ভোট পাবে, যত বদমাশই তুমি হও না কেন। যার যত টাকা বেশি, তার তত ভোট বেশি। যে যত বেশি মিথ্যে বলতে পারে, তত ভোট পাবে বেশি। আমি উদাস বসেছিলাম জানালায় মাথা রেখে। এলোমেলো ভাবনার মধ্যে ডুবে। সাহাবুদ্দিনের ডাকে আমি চমকে উঠি। বাড়ি এসে গেছে। সাহাবুদ্দিন দাঁড়িয়ে আছেন দরজা খুলে।
বেরিয়ে আসতে আসতে বলি, ‘আপনাকে না কতদিন বলেছি দরজা খুলে দেবেন না গাড়িতে ওঠার সময়, বেরোবার সময়!’
সাহাবুদ্দিন মাথা নত করেন।
ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবি, সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে এই যে আমি এই ভদ্রতা করছি, তা কেন করছি, আমার নিজের জন্য নাকি সাহাবুদ্দিনের জন্য! নিজের জন্য নিশ্চয়ই, নিজে আমি খানিকটা উদার হয়েছি ভেবে আমার ভাল লাগে, সেই ভাল লাগাটি আমি আমাকে দিতে চাই।
সাহাবুদ্দিনের জন্য দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও পরিশ্রমের কাজ নয়। এটি করে তিনি আমাকে সন্তুষ্ট রাখতে চান, আমি যেন তাঁকে খুব সহজে বলে না দিতে পারি, আপনার চাকরি আজকের মত এখানেই শেষ। চাকরিটি সাহাবুদ্দিনের দরকার। সাহাবুদ্দিন গাড়ির তেল চুরি করছে না, আমাকে ঠকিয়ে পয়সা কামাতে চাইছে না, কারণ তাঁর মধ্যে কোথাও কোনও সৎ একটি মানুষ লুকিয়ে আছে, ছোটবেলায় কখনও হয়ত শিখেছিলেন, অন্যায় করিও না, মানুষের মনে কষ্ট দিও না, অসৎ পথে চলিও না এসব নীতিবাক্য। বুড়ো হয়ে গেছেন, আজও শৈশবের উপদেশবাণী মেনে জীবন কাটাচ্ছেন যখন বেশির ভাগ মানুষই ওসব হয় ভুলে গেছে, অথবা ভুলে না গেলেও মেনে চলা জরুরি মনে করে না, অথবা মেনে চলতে চাইলেও নিজের চাহিদা আর চারপাশের দূর্নীতি তাদের ওসব মেনে চলতে দেয় না। ওসব এখন পুরোনো কথা, বাজে কথা।
লেখার ঘরে ঢুকে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসি। মাথার ভেতর পোকার মত নানান ভাবনা কিলবিল করছে। কত লেখা অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে, শেষ করতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় কী হবে লিখে! কী দরকার লিখে! একটি বিচ্ছিরি হতাশা আমাকে গ্রাস করে রাখে। আমার এসব লেখায় সমাজের কোনও পরিবর্তন হবে না, তবে আর লেখা কেন! দেশের আশি ভাগ মানুষ লিখতে পড়তে জানে না। আমার লেখা শিক্ষিতরাই কেবল পড়ার সুযোগ পায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সমস্যা নিয়েই লিখি বেশি। কারণ আমি এদেরই দলের লোক। আমি খুব দরিদ্রের ঘরে পৌঁছতে পারি না, শারীরিক ভাবে না, মানসিক ভাবেও না। আমি কেবল কল্পনা করতে পারি তাদের জীবন, আমি তাদের সত্যিকার একজন হতে পারি না। আমি নূরজাহানের কথা লিখি, লিখি কারণ খবরের কাগজে নূরজাহানের যন্ত্রণা পড়ে সেই যন্ত্রণা আমি অনুভব করেছি। আমি কিন্তু নূরজাহানের জীবন যাপন করে সেই যন্ত্রণা অনুভব করিনি। দুই অনুভবের মধ্যে একটি বড় ফারাক আছে। আমি কি আসলে আমার নিজের জন্য নূরজাাহানকে ব্যবহার করছি! নাকি আমি সত্যি সত্যিই নূরজাহানের কষ্ট বুঝতে চাইছি। নূরজাহানের কথা আমি লিখি কেন! কজন নূরজাহান আমার লেখা পড়তে পারে,পড়ে মনে শক্তি পেতে পারে! একজনও না। আমি কি তবে আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের জন্য লিখি, যেন পড়ে আমাকে বাহবা দেয়, নাকি আমি তাদের ভেতরে আমার যে অনুভব সেই অনুভবটিকে ছড়িয়ে দিতে চাই, যেন তারা শোয়া থেকে বসে থাকা থেকে উঠে দাঁড়ায়, যেন কিছু ভাল কিছু একটা করার জন্য উদ্যোগী হয়! আমি ঠিক বুঝে পাই না, কী প্রয়োজন এই দেশটির জন্য। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হলেই সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হবে, ধর্মের রাজত্ব যাবে, শিক্ষা চিকিৎসা সব ব্যবস্থার উন্নতি হবে! নাকি একটি সুস্থ রাজনৈতিক অবস্থা এলেই সমাজ সুস্থ হবে! নাকি ধর্মীয় আইনের অবসান হলেই সব সমস্যা দূর হবে! কোনটি? এর কোনটি নারী পুরুষের বৈষম্য, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর বৈষম্য, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করতে পারে! কেবল একটি পরিবর্তনই কি যথেষ্ট, যেহেতু একটির সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক ওতপ্রোত! নাকি আলাদা আলাদা করে একই সঙ্গে সব কিছুর জন্য লড়াই করতে হবে! ধুত্তুরি বলে আমি উঠে পড়ি চেয়ার থেকে। চা খাওয়া দরকার। চায়ের জন্য মিনুকে ডাকি। মিনু দৌড়ে রান্নাঘরে চলে যায় আমার জন্য চা বানাতে। আজকে মিনু তো গার্মেন্টসএ কাজ করতে পারত। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু মিনুকে কেন দিচ্ছিন! গার্মেণ্টেসএ কাজ করতে! আমার আরামে আয়েসে অসুবিধে হবে বলে! নাকি মিনুর মঙ্গলের কথা ভাবছি আমি! গার্মেন্টসএর মেয়েরা যে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, সেই নিরাপত্তাহীনতা এখানে মিনুর নেই, সেটি ভাবছি।
নাহ, চা না খেলে আমার মাথা থেকে এসব যাবে না, এই প্রশ্নগুলি।
আমি যখন চা খাচ্ছি, তখন আসে সেই পাঁচজন মেয়ে। আগেও একদিন এসেছিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়ে। সাদাসিধে শাড়ি পরা, সাদাসিধে চুলের বিনুনি, কিন্তু কথাগুলো এদের সাদাসিধে নয়। এদের কথা আগেরবারের মতই। আমি এই যে মেয়েদের স্বাধীনতার বিষয়ে লিখছি, এভাবে লিখে কোনও লাভই হবে না, যদি পুঁজিবাদী সমাজ টিকে থাকে। সুতরাং আমাকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে হবে, আমাকে পার্টিতে সক্রিয় হতে হবে, এই পার্টি যদি ক্ষমতায় আসে, তবেই আমার স্বপ্নগুলো বাস্তবে পরিণত হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।
নাহ, আমি কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে চাচ্ছি না।
কেন?
যেহেতু রাজনীতি আমি বুঝি কম।
মেয়েরা আমার সঙ্গে অনেকটা একমত হয় যে আমি রাজনীতি বুঝি কম।
চা আসে। পাঁচজনের সামনে চা ঠাণ্ডা হতে থাকে। পাঁচজনই চা পানের চেয়ে বেশি আগ্রহী কথা বলতে।
আমি কেন আলাদা করে ধর্মহীনতার কথা বা নারী স্বাধীনতার কথা লিখছি! আমি কেন কেবলই কমিউনিজমের কথা লিখছি না, কারণ কমিউনিজম এলেই আপনা আপনি নারী স্বাধীনতা আসবে, ধর্ম দূর হবে। আমি যে সমস্যাগুলো তুলে ধরছি, সেগুলো সুপারফিসিয়াল সমস্যা। আমি লিখছি ঠিকই সমস্যা নিয়ে, কিন্তু কোনও সমস্যারই গোড়া পর্যন্ত যাচ্ছি না, সমস্যার মূলটিকে চিহ্নিত করছি না। মেয়েরা আরও আরও সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলে, সব কিছুর কারণই হল পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা।
খুক খুক করে হঠাৎ কেশে উঠি। কাশি পায় বলেই কাশি। কাশির সঙ্গে হঠাৎ হাসিও পায় কারণ পাঁচজনের একজন যখন জিজ্ঞেস করে, কাশি হয়েছে কেন?, আমি প্রায় বলতে নিচ্ছিল!ম, পুঁিজবাদী সমাজ ব্যবস্থাটিই আমার এই কাশির কারণ।
পাঁচজনের কথা শুনতে শুনতে আমি লক্ষ করি, বাক্যগুলো চমৎকার তাদের। কিন্তু এও লক্ষ্য করি, বাক্যগুলো তাদের মন থেকে বেরোচ্ছে না, বেরোচ্ছে মাথা থেকে। চমৎকার চমৎকার বাক্যগুলো সবে যেন ওরা মুখস্ত করে এল। পাঁচজনের কেউ কারও সঙ্গে কোনও কিছুতে দ্বিমত পোষণ করছে না। একজন কথা বললে চারজন মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছে। পাঁচজনকেই আমার সাদাসিধে রোবটের মত মনে হয়।
ওরা আমাকে দীর্ঘ সময় নিয়ে টন টন উপদেশ দান করে বিদেয় হয়।
আমি বসে থাকি সোফায়, বসেই থাকি। টেলিভিশন ছেড়ে ইয়াসমিন জিটিভির হিন্দি গান শুনছে। টেলিভিশনের দিকে আমার চোখ। কিন্তু আমার মন অন্য কোথাও। যখন সাজু , লাভলি আর জাহেদা এসে আমাকে ডাকে, জিজ্ঞেস করে কেমন আছি, তখনও মন সেই অন্য কোথাও থেকে ফেরেনি। তবে ফেরে যখন জাহেদা আর সাজুর চাকরি গেছে, শুনি। চাকরি যাওয়ার কারণ গার্মেণ্টেসএর মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন। দীর্ঘদিন থেকে ওরা এই আন্দোলন করার কথা ভাবছিল। ওরা শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কী তাদের পাওনা, কী তারা পাচ্ছে না, কী করে মালিক তাদের ঠকাচ্ছে, এসব বলে বলে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কয়েক হাজার শ্রমিককে সচেতন তরে প্রতিবাদী করে রাস্তায় নামিয়েছিল। কিন্তু মালিকের ভাড়াটে গুণ্ডারা মিছিলের শ্রমিকদের পিটিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছে, পুলিশ কোনও গুণ্ডার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করেনি। পনেরো ঘন্টা কাজ করা, সপ্তাহের ছুটি, পরবের উৎসবের ছুটি,ঐচ্ছিক ছুটি কিছুই না পাওয়া, তিন হাজার শ্রমিকের জন্য দুটো মাত্র টয়লেট থাকা, তার ওপর দুবারের বেশি টয়লেট ব্যবহার করার নিয়ম না থাকা, কারও বাচ্চা পেটে এল তো চাকরি যাওয়া, কেউ একদিন অসুখে পড়ে কারখানায় আসতে না পারলে একদিনের মাইনে কাটা, অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনও বাড়তি টাকা না দেওয়া — এসব আগেই আমাকে জানিয়েছিল ওরা। আমি লিখেওছি কারখানার শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে। কিন্তু লিখলেই কি সমস্যা যায়! ওরা যে আন্দোলনটি করছিল কারখানা বন্ধ করে দিয়ে, সেটিরই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শ্রমিকদের মেরে মাথা ফাটিয়ে, পা ভেঙে, হাত ভেঙে দিয়ে নেতাদের চাকরি খেয়ে মালিক বেশ আছে। মালিকের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। আদালত কোনও মামলা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আমি বলি, ‘একটা জিনিস ভাল যে কারখানা বন্ধ থাকবে।’
জাহেদা বলে, ‘কালই কারখানা খুলবে আপা।’
জ্ঞকোনও শ্রমিক যদি কাজ না করে তবে কি করে খুলবে?’
‘অনেক শ্রমিকই মালিকের সঙ্গে আপোস করবে। মালিকের অধীনতা মেনে নেবে।’ জ্ঞকিন্তু সবাই তো মানবে না!’
জ্ঞযারা মানবে না, তাদের তো ছাটাই করেই দিয়েছে। কিন্তু মালিকের অসুবিধে হবে না। দেশে গরিবের সংখ্যা প্রচুর। চাইলেই শ্রমিক পাবে। যে কোনও কনডিশনে কাজ করার জন্য অনেকেই প্রস্তুত।’
জাহেদাকে আমি আমার চোখের সামনে দেখেছি ধীরে ধীরে সচেতন হতে, হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করতে, দাঁতে দাঁত পিষতে। রাতে রাতে শ্রমিকদের সঙ্গে গোপন বৈঠক সেরে জাহেদার দলটি আমার বাড়িতে চলে আসত, ক্ষিধে পেট, তাড়াতাড়ি খাবার আয়োজন করতাম ওদের জন্য। খেতে খেতে বলত কতদূর এগোচ্ছে কাজ, আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে দল ভারী হতে। আজ অনেকদিন হল চাকরি নেই জাহেদা আর সাজুর। লাভলীর চাকরিটি এখনও আছে, তবে এটিও যাবে যে কোনও একদিন। সাজু আর জাহেদা অন্য কারখানায় চাকরির জন্য গিয়েও পায়নি চাকরি। অভিজ্ঞতা আছে গার্মেন্টসএর কাজে, জানার পরও কোনও চাকরি জোটে না। অনেকক্ষণ শুনি তাদের কথা। অনেকক্ষণ বসে থাকি। একসময় উঠে গিয়ে আমি ব্যাংকের চেকবইএর শেষ পাতাটি ছিঁড়ে আনি। সাড়ে চার হাজার টাকা আছে ব্যাংকে, পুরোটাই লিখে দিই জাহেদার নামে।
জাহেদা অবাক, ‘টাকা কেন?’
‘সেলাই মেশিন কেনো। ঘরে বসে সেলাই করে আপাতত কিছু রোজগার কর।’
আমি গিয়েছি পল্লবির বস্তিতে জাহেদার ছোট্ট বেড়ার ঘরটিতে। ঘরটিতে কেবল একটি চৌকি আর একটি ছোট্ট টেবিলের জায়গা হয়। চৌকিতে পা তুলে আসন করে বসে গল্প শুনেছি জাহেদার সাজুর আর লাভলির জীবন সংগ্রামের। জাহেদা কি করে গ্রাম থেকে শহরে এসে বেঁচে থাকার লড়াই করেছে। মাত্র অষ্টম শ্রেণীর বিদ্যে নিয়ে গার্মেন্টসএর শ্রমিক হওয়া ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না তার। সাজু লেখাপড়া করতে পছন্দ করত, মেট্রিক পাশ করেছে, কিন্তু কলেজে পড়া সম্ভব হয়নি অভাবের কারণে, তাই চাকরি করা শুরু করেছে। লাভলিরও প্রায় একই অবস্থা। বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারে সাহায্য করার জন্য তাকে চাকরি করতেই হচ্ছে। সাজু আর জাহেদা একসঙ্গে থাকে কয়েক বছর থেকে, দুজনের একটি বাচ্চাও আছে। বাচ্চাটিকে তারা গ্রামে জাহেদার মার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানে তাদের দুজনই সারাদিন বাইরে, বাচ্চা রাখার কেউ নেই। সাজু খুব গর্ব করে বলে জ্ঞআমরা লিভ টুগেদার করি। বিয়ে জিনিসটা যুক্তিহীন।’
জ্ঞএখানে কোনও অসুবিধে হয় না বিয়ে ছাড়া একসঙ্গে থাকতে?’ আমি জিজ্ঞেস করি। সাজু বলে, ‘না। গরিব আর ধনীদের লিভ টুগেদারে কোনও অসুবিধা নাই। অসুবিধা হয় মধ্যবিত্তদের।’
তা ঠিক, ভাবি, সমস্ত অসুবিধে মধ্যবিত্তের। মধ্যবিত্তের লজ্জা বেশি, ভয় বেশি, যত সংস্কার আছে, সব মানার এবং মানার ভানও বেশি।
সাজুর লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ থাকার কারণে পত্রপত্রিকা যেখানেই যা পায়, পড়ে। পড়তে পড়তেই আমার লেখা ওর নজরে আসে। প্রতি সপ্তাহে তার পড়া চাইই আমি যা লিখি। লাভলী আর জাহেদাসহ অনেককে সে আমার লেখা পড়িয়েছে। এরপর সাজুই প্রথম জাহেদাকে নিয়ে আমার সঙ্গে একদিন দেখা করতে আসে, এরপর লাভলীকে নিয়ে জাহেদা আসে, এরপর ওদের সূত্র ধরে আরও গার্মেন্টসএ শ্রমিক আসে। ওদের সঙ্গে কথা বলে আমার ভেতরে সাহসের জন্ম হয়। ওদের সঙ্গ আমাকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের সঙ্গের চেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। ওদের সাহস এবং মনোবল আমাকে চমকিত করে। বাসের দরজায় ঝুলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে, বাসে চড়ার পয়সা না থাকলে মাইল মাইল পথ পায়ে হাঁটছে, দুপুরের কড়া রোদ মানছে না, রাতের অনিশ্চয়তা মানছে না, হেঁটে যাচ্ছে। ওরা পুঁজিবাদের সংজ্ঞা পড়েনি, সমাজতন্ত্রের কোনও তত্ত্ব কথা জানে না। কিন্তু নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ওরা জানে, কঠোর পরিশ্রম করতে জানে, এবং তার মূল্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় করার জন্য যা কিছু করতে হয় তা করতে জানে। অভাব ওদের মাথাকে নত করেনি। কোনও ষড়যন্ত্র ওদের পিছপা করে না। কোনও আঘাত ওদের থামায় না। ওরা অনেক কিছুতে অজ্ঞ, কিন্তু কোনও কিছুতেই মূর্খ নয়। প্রচণ্ড উদ্যম ওদের। ভয় পেলে ওদের চলে না, কাতর হলে চলে না। ধর্মের ভেদ, নারী পুরুষের ভেদ মানা ওদের চলে না। কারও দেওয়া পথ বা মত মেনে চলে না, নিজেদের পথ ওরা তৈরি করে নেয়। প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করছে, অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের জন্য সংগ্রাম। সংগ্রামী হিসেবে আমার নাম হয়েছে, কিন্তু আমি নিজে বুঝি, আমার মত দশটি তসলিমা যোগ করলেও এক জাহেদার মত সংগ্রামী হতে পারবে না। আমার সাহসকে দশ দিয়ে গুণ করলেও এক জাহেদার সাহসের সমান হবে না। নিজেকে নিয়ে যত গর্ব করি আমি, তার চেয়ে বেশি করি জাহেদাদের নিয়ে।
চেকটি নিয়ে যখন ওরা চলে যায়, হঠাৎ একটি জিনিস আমার মনে উঁকি দেয়, আমি কি ওদের আগুনে কিছুটা জল ঢেলে দিলাম। যে ক্রোধটি ওদের ছিল, তা কি খানিকটা নষ্ট করে দিলাম! এই সুবিধেটুকু দিয়ে ওদের কি আমি শান্ত করে দিলাম। ওরা কি গার্মেণ্টেসএর মালিকদের শোষণের কথা আর কোনও শ্রমিকদের বলবে না, ওদের একত্রিত করবে না! শ্রমিকের অধিকার আদায় করার জন্য ওরা কি আর আন্দোলন করবে না! ওরা কি এখন কেবল সেলাই মেশিন নিয়ে বসে বসে সেলাই করবে আর একটু একটু করে দুজনের, কেবল দুজনের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার কথাই ভাববে! সম্মিলিত মানুষের সংগ্রাম থেকে আমি কি জাহেদা আর সাজুকে সরিয়ে দিলাম! একটি শীত শীত ভয় আমাকে কাঁপাতে থাকে।
বছর চলে যাচ্ছে। এ সময় ব্যস্ততার শেষ নেই। দিন রাত আমি লেখায় ব্যস্ত। প্রুফ দেখায় ব্যস্ত। সামনে ফেব্রুয়ারি। ফেব্রুয়ারি মানেই হচ্ছে বইমেলা। মেলায় বই প্রকাশের জন্য প্রকাশকেরা উন্মাদ হয়ে ওঠেন। পত্রিকার কলামগুলো নিয়ে কাকলি প্রকাশনী থেকে বের হচ্ছে ছোট ছোট দুঃখ কথা। কাকলির সেলিম আহমদ আমার অনুরোধ রেখেছিলেন ফ্যান দাও বইটি বের করে। ফ্যান দাও পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় লেখা কবিতার সংকলন। সেই সময়ের পত্র পত্রিকা ঘেঁটে যে সব কবিতা পেয়েছি, সেই ভুলে যাওয়া কবিতা গুলো নিয়ে বই সম্পাদনা করেছি। এটি করার জন্য আমাকে প্রেরণা দিয়েছিলেন নিখিল সরকার। তিনজনের ওপর তিনটি বইয়ের কাজটি ভাগ করে দিয়েছেন তিনি। সে সময় গল্পলেখকরা মন্বন্তরের ওপর যেসব গল্প লিখেছিলেন, সেগুলো সংকলিত করার দায়িত্ব বেলাল চৌধুরীর ওপর, আমার ওপর কবিতার, আর নিখিল সরকার নিজে নিয়েছেন মন্বন্তরের ছবি নিয়ে বই করার দায়িত্ব। মন্বন্তরের সময় শিল্পীদের আঁকা আঁকা ছবিগুলো যোগাড় করেছেন, ছবি নিয়ে লেখা তাঁর বড় একটি প্রবন্ধ যাচ্ছে বইটিতে। বইটির নাম দায়। বইগুলো পুনশ্চ নামের ছোট একটি প্রকাশনী থেকে বেরোয়। ফ্যান দাও বইটি খুব একটা চলবে না জেনেও সেলিম আহমদ বইটি প্রকাশ করেন আমার অনুরোধে, অনুরোধে ঢেঁকি গিললে পরে আনুকূল্য লাভের সম্ভাবনা আছে বলে। কাকলি প্রকাশনী তাই নতুন একটি নতুন বই পেয়েছে আমার। পার্ল পাবলিকেশনের ভাগ্যে শিকে তেমন ছেড়েনি, তাঁকে দিয়েছি লজ্জা এবং অন্যান্য নামের একটি বই, এটি আমার লেখা বই নয়, তবে লজ্জা নিয়ে অন্য লেখকরা যা লিখেছেন, সেসবের সংকলন। পার্ল পাবলিকেশনের মিনু খুব মন খারাপ করেছেন, বলেছেন, ‘অরিজিনাল কিছু দেন।’
‘অরিজিনাল কোত্থেকে দিই এখন!’
ব্যস্ত ছিলাম কোরানের নারী লিখতে, বেদ বাইবেল কোরান ঘাঁটায়। আমার মেয়েবেলা নামে একটি উপন্যাস এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। অসম্পূর্ণ জিনিস তো কাউকে দেওয়া যায় না। মিনুকে শেষ পর্যন্ত পুরোনো চারটে উপন্যাস জড়ো করে ছাপতে বলি, চারকন্যা নাম বইয়ের। মিনুর মুখে একটু হাসি ফোটে, কিন্তু তারপরও আমাকে মনে করিয়ে দেন, নতুন বই কিন্তু আমি পাই নাই। খোকা যেসব বই ছেপেছিলেন, সেগুলো প্রকাশ করার দায়িত্ব এক এক করে বিভিন্ন প্রকাশককে দিয়ে দিই। দুঃখবতী মেয়ে নামে ছোট গল্পের একটি বই মাওলা ব্রাদার্সকে দিই। বহুদিন থেকে ঘুরছেন মাওলার প্রকাশক। কাউকে মন খারাপ করে দিতে ইচ্ছে হয় না। সবাইকে মনে হয় কিছু না কিছু দিই। কিন্তু সাধ্য কোথায়! জ্ঞানকোষ প্রকাশনীর প্রকাশক লোকটি অত্যন্ত অমায়িক, তাঁকে আমার নির্বাচিত কলামটি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছি। এটি পেয়ে তিনি মহাখুশি, যদিও বইটি পুরোনো। সবাইকে আমার কথা দিতে হয় নতুন বই লেখা হলেই তাদের দেব। অংকুর প্রকাশনীর মেজবাহউদ্দিন আহমেদের করুণ মুখটি দেখে মায়া হয়। তিনি বলেন, আজ থেকে পাঁচ বছর আগে মিলনকে উপন্যাস লেখার জন্য অগ্রিম টাকা দিয়েছেন, আজও মিলন কোনও বই দেয়নি। তিনি সমীক্ষণ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাপতেন, সমীক্ষণে আমি নিয়মিত লিখতাম। সে কারণে মেজবাহউদ্দিনের সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি প্রকাশনা ব্যবসায় নামার পর থেকে বই চাইছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরামর্শ দিই পত্রিকায় পক্ষে বিপক্ষে যেসব লেখা বেরিয়েছে, ওগুলো প্রকাশ করে যেন তিনি আপাতত সন্তুষ্ট থাকেন। কোনও নতুন বই নেই? আছে একটি বই। কোরানের নারী। সব প্রকাশকই নাম শুনে আঁতকে উঠেছেন। কেউ এই বইটি প্রকাশ করার সাহস পাননি।
প্রকাশকদের এমন ভিড়ে আমার বারবারই পুরোনো সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। যখন কেবল একজন লেখক এবং একজন প্রকাশকের মধ্যে কথা হত। পরিকল্পনা হত। দুজনের শ্রম এবং স্বপ্ন থেকে একটি বইয়ের জন্ম হত। খোকার সঙ্গে সেই আমার দিনগুলো। কী ভীষণ আবেগ ছিল তখন, কী প্রচণ্ড উত্তেজনা ছিল! সেই দিনগুলো এখনকার এই ভিড়ভাট্টার দিনের চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল। খোকার কথা আমার খুব মনে পড়ে। আমার দুঃসময়ের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। সুসময় এল, সব আছে, তিনিই কেবল নেই। খোকার সঙ্গে কোনওদিন আমার সম্পর্ক নষ্ট হবে আগে ভাবিনি। কিন্তু হয়েছে। এর পেছনে কারণটি খোকাই। একদিন তিনি হঠাৎ আমার হাত ধরে জ্ঞআপনি কি কিছুই বোঝেন না, আমার ভালবাসা আপনি কেন বোঝেন নাঞ্চ বলে কেঁদে উঠেছিলেন, আমি হতচকিত বিস্ময়ে বোবা হয়ে ছিলাম, এও আমাকে দেখতে হল! জীবনে অনেক অপমানকর, অনেক লজ্জাকর, অনেক ঘৃণ্য দৃশ্য আমি কল্পনা করেছি, কিন্তু এই দৃশ্যটি আমার চরম দুঃস্বপ্নের মধ্যেও আসেনি কোনওদিন! আর সইছিল না আমার। মনে হচ্ছিল মাথা ঘুরে এক্ষুনি বুঝি আমি পড়ে যাবো, মুচ্ছগ! যাবো। দ্রুত নিজের হাত টেনে নিয়ে খোকার সামনে থেকে সরে গিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছি। খোকা যে কখনও আমার প্রেমে পড়ে আমাদের চমৎকার বন্ধুত্বটির এমন সর্বনাশ করে দেবেন কোনওদিন, কে জানতো! খোকাকে বের করে দিয়ে আকুল হয়ে কেঁদেছি। স্বপ্ন ভেঙে গেলে মানুষ যেমন শূন্য বোধ করে, কাঁদে, আর্তনাদ করে, তেমন করে। এরপর থেকে খোকা আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেননি। এই ঘটনার বেশ কয়েকমাস আগে খোকার বউ আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন যে খোকার সঙ্গে বোধহয় আমার গভীর প্রেম চলছে, তখন খোকা নিজেই আমাকে বলেছিলেন তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর বউকে যেন আমি আমাদের সম্পর্কের ব্যপারে জানিয়ে আসি, যেন তাঁর ভুল ভাঙে। তাই করেছিলাম। করার পর খোকার বউ আমার বাড়িতে খোকার সঙ্গে অথবা একাই মাঝে মাঝে চলে আসতেন। গল্প হত। খাওয়া দাওয়া হত। পত্রিকায় সাংবাদিকরা আমার সঙ্গে খোকার বিয়ে দিয়েছে কতবার, বাংলাবাজারের প্রকাশকরা কত অপদস্থ করেছে খোকাকে। কিন্তু কিছুই আমাদের সম্পর্ককে এতটুকু ম্লান করেনি। কিন্তু খোকা নিজেই কী না শেষ পর্যন্ত সব তছনছ করে দিলেন!
আগের জীবন আর নেই। সেই উত্তেজনার জীবন। পঈচ্ছদজ্ঞশল্পী হিসেবে তখন সমর মজুমদার আর ধ্রুব এষ খুব ভাল করছে। খুব কাছ থেকে ওঁদের কাজ দেখেছি। এলিফেন্ট রোডে সমরের বাড়িতে গিয়ে সমরের পঈচ্ছদ আঁকা দেখতাম, আর্ট কলেজের হোস্টেলে থাকতেন ধ্রুব এষ। ধ্রুব আমার কবিতার বইয়ের প্রতি পাতার জন্য স্কেচ করতেন রাত জেগে। সমরের পঈচ্ছদ ভাবনার মধ্যে আমার ভাবনাগুলো মিলিয়ে দেখতাম কেমন দেখায়। একটি ভাল না লাগলে আরেকটি, আরেকটি না লাগলে আরেকটি। এরকম যোগ বিয়োগ চলত। ক্লন্তি ছিল না কিছুতে। ধ্রুব হল কি কাজ? না, আজ হয়নি, কাল হবে। কাল আবার ধ্রুবকে শহর খুঁজে ধরা। ধ্রুব এটা খুব সুন্দর হয়েছে, ওটায় আরেকটু রং হলে ভাল হয়। এখন কে পঈচ্ছদ করছে, কেমন হচ্ছে পঈচ্ছদ তার খোঁজ রাখি না। পরিধি যত বাড়ছে, আমার চলাচল তত সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। আগের সেই আবেগ, সেই উত্তেজনা চাইলেও ফিরে পেতে পারি না এখন।
ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে উৎসব শুরু হয়ে গেছে। পুরো মাস জুড়ে চলবে উৎসব। বইমেলা, জাতীয় কবিতা উৎসব, কবিতা পাঠ, কবিতা আবৃত্তি, গানের মেলা, নাট্যোৎসব। সারা বছর লেখকেরা এই একটি মাসের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। শিল্পী সাহিত্যিক পাঠক দর্শক শ্রোতা সব এসে জড়ো হন একটি জায়গায়। এই মাসটির জন্য আমিও অপেক্ষা করে থাকি। কিন্তু ঘরে বসে আছি আমি। কোথাও আমি আমন্ত্রিত নই। কেবল আমারই কোথাও যাবার অনুমতি নেই। কেউ আমাকে কোথাও অংশগ্রহণ করার জন্য ডাকে নি। সাধারণ দর্শক হিশেবেও আমি সকল জায়গায় অনাকাঙ্খিত। কবিরা এক অনুষ্ঠান শেষ করে আরেক অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন। আনন্দের জোয়ার তাঁদের ভাসিয়ে নিচ্ছে আরও অধিক আনন্দের দিকে। আমিই কেবল একা একটি অন্ধকার ঘরে বসে আছি। সকলে বাইরে, প্রতিদিন বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত উৎসবে। আমি জানি আমি যদি মেলার দিকে যাই, আমার চারপাশে ভিড় জমে যাবে। ভিড়ের একটি দল আমাকে মেরে ফেলতে চাইবে, আরেকটি দল আমার পায়ের ধুলো নিতে চাইবে। একদল আসবে ছুরি হাতে, আরেকদল বই হাতে, অটোগ্রাফ নিতে। আমার তবু ইচ্ছে করে ছুটে যাই, সেই আনন্দের দিকে সব মুত্যুভয় তুচ্ছ করে ছুটে যাই। মরলে মরব। তবু যাই। কিন্তু পারি না। অদৃশ্য একটি শেকল আমার পায়ে।
কবিবন্ধুরা ব্যস্ত। কারও সময় নেই আমার খবর নেবার, কেমন আছি আমি, উৎসবে যেতে না পারার কষ্টে কেমন ভুগছি। জাতীয় কবিতা উৎসব হচ্ছে, পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে বইমেলা হচ্ছে, কবিতাপাঠ হচ্ছে। আমিই খবর নিই, জিজ্ঞেস করি, কেমন হচ্ছে মেলা? চমৎকার হচ্ছে, দারুন হচ্ছে, আজ এই হল, কাল এই হল এসবের দীর্ঘ বর্ণনা শুনি। আবৃত্তির নতুন ছেলে মেয়েরা আমার কবিতা আবৃত্তি করে, বইয়ের অংশ থেকে পাঠ করে, কলাম পাঠ করে ক্যাসেট বের করেছে। ক্যাসেটগুলো হাতে আসে। প্রকাশকরা খবর দেন, আমার বইয়ের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মুদ্রণ হয়ে গেছে এর মধ্যেই। ছেপে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না, এত বিক্রি হচ্ছে। জানান যে অনেকে আসে লেখকের খোঁজে, অটোগ্রাফ চায়।
‘আমার যে যেতে ইচ্ছে করছে।’ ব্যকুলতা আমার কণ্ঠে।
শুনে প্রকাশকরা জিভে কামড় দেন, ‘এ কথাটি মুখেও নেবেন না। বিপদ তো আছেই। তাছাড়া মেলা কমিটির লোকেরা আপনাকে মেলায় ঢুকতে দেবে না, সে তো জানেনই।’
একুশে ফেব্রুয়ারির দিন ভোরবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি খালি পায়ে ছেলেরা মেয়েরা শাদা পোশাক পরা, হাতে ফুল আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গাইতে গাইতে যাচ্ছে শহীদ মিনারের দিকে। এরকম আমিও যেতাম। আমিও প্রতি একুশেতে ফুল দিতাম শহীদ মিনারে। আজ শহরের সব লেখক কবি, সব শিল্পী সাহিত্যিক উৎসবে ব্যস্ত, অটোগ্রাফ দিচ্ছেন, কবিতা পাঠ করছেন, চা খেতে খেতে অনুরাগী পাঠক বা লেখক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। অনেকদিন দেখা না হওয়া কত শত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, কত সাহিত্যিক আলোচনা হচ্ছে বিশ্ব সাহিত্য পরিষদের মাঠে, বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে। আমিই কেবল একা। আমিই কেবল বঞ্চিত সবকিছু থেকে। আমারই কেবল অধিকার নেই কোনও আনন্দ পাওয়ার। জানালার গ্রিলে মাথা রেখে দেখতে থাকি গান গাইতে গাইতে হেঁটে যাওয়া মানুষ। যত দূর চোখ যায়, কেবল মানুষ। কী আশ্চর্য সুন্দর যে হয়ে ওঠে ফাল্গুনের এই দিনটি! চারদিকে কৃষ্ণচূড়ার লাল, আর কণ্ঠে কণ্ঠে করুণ এই সুর। সুরটি আমাকে কাঁদাতে থাকে। আমি বিছানায় উপুড় হয়ে গুলিবিদ্ধ মানুষের মত পড়ে থাকি। নিজেকে সত্যিই মৃত মনে হয়। মৃতই মনে হতে থাকে। তখন একটি হাত আলতো করে আমার পিঠ স্পর্শ করে। বুঝি, এটি মার হাত। মা কোমল কণ্ঠে বললেন, ‘আজকে আমি তোমার হইয়া শহীদ মিনারে একটা লাল গোলাপ দিয়া আসব।’
ফেব্রুয়ারি শেষ হলে আবার আমার বন্ধুদের আনাগোনা শুরু হয় আমার বাড়িতে। শামসুর রাহমান কিছুদিন খুব ঘন ঘন আসেন। আড্ডা আলোচনা নেমন্তন্ন এসব কারণ তো আছেই, আরেকটি নতুন কারণ যোগ হয়েছে। সেটি প্রেম। শামসুর রাহমান প্রেমে পড়েছেন নিজের গোড়ালির বয়সী এক মেয়ের। কয়েকটি পাগল করা প্রেমের কবিতাও লিখে ফেলেছেন এর মধ্যে। কে এই মেয়ে যাকে নিয়ে এত কাব্য! মেয়ে রাজশাহীর, নাম ঐশ্বর্যশীলা। ঐশ্বর্যশীলাকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাজিম মাহমুদ একদিন ঢাকায় আসেন। সুন্দরী মেয়ে, বিয়ে হয়েছে, চার বছর বয়সী একটি পুত্রসন্তানও আছে। ঐশ্বর্যশীলা আমার বাড়িতে থাকবে কদিন। নাজিম মাহমুদ থাকবেন তাঁর কন্যার বাড়িতে। কন্যা অধ্যাপক স্বামী নিয়ে ঢাকা শহরে থাকে। ঐশ্বর্যশীলা এসেছে এ খবরটি পেয়ে শামসুর রাহমান চলে আসেন আমার বাড়িতে। দুজনে যখন নিভৃতে কথা বলছেন, আমি বারান্দার অন্ধকারে বসে প্রেম নিয়ে ভাবি। প্রেমে পড়ার কোনও বয়স নেই, আসলেই নেই। একুশ বছরে বয়সী মৃগাংক সিংহ আর আটান্ন বছর বয়সী শরিফা খাতুন মিনা প্রেম করে বিয়ে করেছে। মৃগাংক আর মিনার সঙ্গে আমার পরিচয় নির্মলেন্দু গুণের মাধ্যমে। মিনা তাঁর বনানীর বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন করেছে কয়েকদিন। আমার বাড়িতেও নতুন দম্পতি বেড়াতে আসে। খুব বেশি কোথাও মিনা আর মৃগাঙ্ক যেতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর বয়সের এই পার্থক্য দেখে লোকেরা হাসে বলে। আমি যদিও সাদরে বরণ করেছি ওঁদের, কিন্তু আমার সংশয় হয়, মৃগাঙ্ক এই বিয়েটি মিনার দৌলতের কারণেই করেছে। মৃগাঙ্ক অজপাড়াগাঁর এক দরিদ্র কৃষকের ছেলে। সুদর্শন। সবল সুঠাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে, সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে উপন্যাস লিখছে। মিনা একটি প্রকাশনী শুরু করেছে মৃগাঙ্কর বই প্রকাশ করার জন্য। মিনা ধনী। তাঁর ছেলে মেয়ে আমেরিকায় থাকে, নিজেও তিনি আমেরিকা যান মাঝে মাঝে, হাতে গ্রীন কার্ড। মিনাকে নিজের আত্মীয় স্বজন সব বিসর্জন দিয়ে এই বিয়েটি করতে হয়েছে। বিয়ের পর মাথায় ঘোমটা পরে তিনি স্বামী সহ শ্বশুর বাড়িও ঘুরে এসেছেন। আমার সংশয় হয়, মৃগাঙ্ক একদিন মিনার টাকা পয়সা সব ভোগ করে, পারলে আমেরিকা পাড়ি দেবার সুযোগ করে নিয়ে মিনাকে ছেড়ে চলে যাবে। আমার আশঙ্কার কথা গুণকে জানিয়েছি, গুণেরও অনেকটা এরকম সংশয়। শামসুর রাহমান আর ঐশ্বর্যশীলার প্রেম বিয়ে পর্যন্ত গড়াবে না, এ আমি নিশ্চিত। শামসুর রাহমান জীবনে আরও মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। প্রেমে পড়ে আশ্চর্য সুন্দর সব কবিতা লিখেছেন। ঐশ্বর্যশীলার কথা ভেবেও তিনি কবিতা লিখবেন। সাহিত্যের ভাণ্ডার আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবেন। ঐশ্বর্যশীলা রাজশাহীতে স্বামীর সঙ্গে বাস করবে, স্বামীটি, ঐশ্বর্য নিজেই বলেছে, অসম্ভব ভাল। আমার মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে, ঐশ্বর্য কি আসলেই শামসুর রাহমানের প্রেমে পড়েছে? নাকি দেশের প্রধান কবির খ্যাতির প্রেমে পড়েছে সে! তাকে নিয়ে শামসুর রাহমানের লেখা কবিতাগুলো পড়ে অভিভূত সে, ওটিই তার সবচেয়ে বড় পাওয়া। একজন কবিকে আবেগস্পন্দিত করে, আলোড়িত করে, কবির হৃদয়োচ্ছঅ!স জাগিয়ে সে নিজের জীবনকে সার্থক করছে।
প্রেম করা কোনও দোষের ব্যপার নয়, প্রেমে মানুষ যে কোনও বয়সেই পড়তে পারে। আমারও মাঝে মাঝে খুব প্রেম করতে ইচ্ছে করে। কোনও উতল প্রেমে যদি একবার ভাসতে পারতাম! ইচ্ছেটি আমার বুকের ভেতর কোথাও গোপনে লুকিয়ে থাকে, বুঝি না যে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ মন যখন খুব উদাস হয়ে আসে, একা বসে থেকে থেকে ইচ্ছেটিকে টের পাই, ইচ্ছেটিকে আলতো করে তুলে নিয়ে ইচ্ছেটির গায়ে আমি নরম আঙুল রাখি। জীবনের রূঢ়তা, ক্রূরতা থেকে ইচ্ছেটির পেলব শরীর আমি আড়াল করে রাখি। রূপবান রুচিবান রসজ্ঞ আলমগীরকে দেখে কদিন রঙিন হয়েছিলাম। আলমগীরের বিয়ে ভেঙে গেছে, এখন নতুন করে সে একটি প্রেম এবং একটি বিয়ের কথা ভাবছে। তার হৃদয়ের দরজা হাট করে খোলা। দরজা খোলা থাকলে যাতায়াত করা যায়, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে গেলেই অস্থির লাগে। আলমগীরের প্রেমে আমি পড়তে পড়তেও পড়িনি। ভাল লাগে তার সঙ্গ, এটুকুই। কায়সারের সঙ্গে সম্পর্কটি এখন সাদামাটা শারীরিক সম্পর্ক। কায়সারকে আমার পেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তার জন্য আমার মন কেমন করে না। প্রেমের ইচ্ছেটি গুনগুন করে আমাকে গান শোনাচ্ছে যখন, মনে পড়ে সেই কলেজ জীবনের হাবিবুল্লাহকে। আমাকে কী উন্মাদের মতই না ভালবাসত হাবিবুল্লাহ ! যখন সে জানল যে আমি তাকে ভালবাসি না, ভালবাসি রুদ্রকে, সে নাওয়া খাওয়া লেখাপড়া সব ছেড়ে দিয়ে লাইলির জন্য যেমন হয়েছিল মজনু, তেমন হয়ে উঠেছিল। দাড়ি কাটে না, চুল কাটে না, ক্লাস করে না, পরীক্ষা দেয় না, দিলেও একের পর এক ফেল করতে থাকে। আমার নাম জপতে তার দিন যায়, রাত যায়। একদিন রুদ্রকে হাতের কাছে পেয়ে মাথায় রক্ত চেপেছিল ছেলের, রুদ্রকে সে মেরেছিল, সত্যিকার মেরেছিল, বলেছিল, আর যদি কোনওদিন তাকে সে দেখে কলেজ এলাকায়, তবে খুন করবে। সেই হাবিবুল্লাহ। এ জীবনে একজনই আমাকে সত্যিকার ভালবেসেছিল। এতটা জীবন পেরিয়ে, এতটা বয়স পেরিয়ে সেই ভালবাসা আমার ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। হাবিবুল্লাহ যদি আমাকে আগের মত ভালবাসতে পারে, তবে আমি এবার আর তাকে ফিরিয়ে দেব না। আমিও বাসব ভাল। আসলে ভালবাসলে ওরকম ভাবেই বাসতে হয়। ওরকম তীব্র করে, ওরকম জগত সংসার তুচ্ছ করে। বাধভাঙা প্রেমের জোয়ারে ভাসতে আমার সাধ জাগে। হাবিবুল্লাহ কেমন আছে, কোথায় আছে কিছুই জানি না। আমার গোপন ইচ্ছেটি তার খোঁজ করে, করে করে একদিন মেলে খোঁজ। হাবিবুল্লাহ নামের একজন ডাক্তার ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চাকরি করে। ময়মনসিংহ মেডিকেল থেকে পাশ করেছে। এ নিশ্চয়ই সেই হাবিবুল্লাহ। পঙ্গু হাসপাতাল ফোন করে করে আমি তাকে পাই। ফোনেই কথা হয় হাবিবুল্লাহর সঙ্গে। এই হাবিবুল্লাহ সেই হাবিবুল্লাহই। আমার ফোন তার কাছে অপ্রত্যাশিত। বাড়িতে আসতে বলি তাকে। এক সন্ধেয় সুদর্শন যুবকটি আমার বাড়িতে এসে হাজির হয়। আগের মতই আছে। এতটুকু পরিবর্তন নেই। প্রথমেই সম্বোধন নিয়ে আড়ষ্টতা। আমরা তুই বলতাম পরষ্পরকে। কিন্তু হাবিবুল্লাহ তুমি বলে সম্বোধন করার পর আমার জিভে তুই তুমি আপনি কিছুই আর আসে না। অতপর ভাববাচ্যের আশ্রয় নিই। ভাববাচ্যে খুব বেশিদূর কথা এগোতে চায় না। থেমে থেমে যায়। দুচারটে কথা হওয়ার পর হাবিবুল্লাহ তার জীবনের দুটো সুখবর দেয়, সে বিয়ে করেছে, তার দুটো বাচ্চা আছে। যে তুফান বইছিল, সেটি হঠাৎ থেমে শান্ত হয়ে যায়। স্তব্ধ চরাচর জুড়ে কেবল জল পড়ার টুপটুপ শব্দ, কোথাও কেউ নেই, অসহ্য নির্জন চারদিক। কেন অবাক হই! আমি কি মনে মনে ভেবেছিলাম যে হাবিবুল্লাহ আমার বিরহে চিরকুমার থেকে গেছে। হ্যাঁ ভেবেছিলাম বৈ কি। দূরাশাকে আশার মত দেখতে লেগেছে।
‘তোমার ভাবীকে বললাম, পুরোনো এক কলেজ-ফ্রেণ্ডএর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি..’
‘আমার ভাবী?’ বিস্ময়ে তাকাই, হাবিবুল্লাহর সঙ্গে কখন হাসিনা বা গীতার দেখা হল! হাবিবুল্লাহ লাজুক হেসে বলল, ‘আমার ওয়াইফ।’
ও। মুখে আমার মলিন হাসি সামাজিক কথাবার্তার নিয়মের সঙ্গে বহুদিন আমার সম্পর্ক নেই। কী জানি, কখনও কি ছিল!
হাবিবুল্লাহ নিজের চাকরি, নিজের সংসার ইত্যাদির গল্প বলে। আর ক্ষণে ক্ষণেই আমার প্রসঙ্গে বলে, ‘তুমি তো খুব বড় হয়ে গেছ। অনেক টাকা পয়সা করেছো। আমাদের এই ডাক্তারি চাকরি করে আর কত পয়সা পাওয়া যায়! জীবন চলে না।’
বাড়িটি গোল গোল চোখ করে দেখতে দেখতে বলে, বাড়িটা কিনেছো বুঝি?’
‘হ্যাঁ।’
‘অনেক দাম তো নিশ্চয়ই। আমার কি আর বাড়ি কেনার সামর্থ হবে?’
‘কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে।’
‘আরে নাহ! যে টাকা পাই, সে টাকা তো খাবার খরচেই চলে যায়। বাপের বাড়িতে থাকি.। তাই চলতে পারছি।’
‘বাপের বাড়িতে থাকলে অসুবিধে কি? নিজের বাড়ি হতেই হবে, এমন কি কোনও কথা আছে!’
‘তোমার তো গাড়িও আছে নিশ্চয়ই।’
‘হ্যাঁ আছে।’
‘বেশ টাকা করেছো।’
‘নাহ। খুব বেশি না। আর.. টাকা পয়সা কি সুখ দেয় নাকি? সুখটাই জীবনে বড়। সুখের সঙ্গে টাকা পয়সার সম্পর্ক নেই।’
‘তোমার ভাবী খুব ভাল মেয়ে। তাকে নিয়ে আমি সুখে আছি। তা বলতে পারো।’
‘এ কি প্রেমের বিয়ে?’
‘নাহ। অ্যরেঞ্জড ম্যারেজ।’
‘বউ কি ডাক্তার?’
‘না, ডাক্তার না। বি এ পাশ করেছে।’
‘চাকরি বাকরি করছে নিশ্চয়ই।’
‘না। তোমার ভাবী হাউজওয়াইফ।’
হাবিবুল্লাহ তার পকেটের মানিব্যাগ থেকে বউ বাচ্চার ছবি বের করে। দেখায়।
‘বউ তো বেশ সুন্দর!’
হাবিবুল্লাহ হেসে বলে, ‘আগে আরও সুন্দর ছিল। এখন তো বাচ্চা টাচ্চা হওয়ার পর ..’
আমার লেখার ঘরে, এমন কী শোবার ঘরেও দুজনে নিরালায় বসে থেকে দেখেছি হাবিবুল্লাহ আমার দিকে কখনও প্রেম চোখে তাকায়নি। কখনও সে পুরোনো সেই দিনের কথা তোলেনি। যত আমি অতীতে ফিরি, সে তত বর্তমানে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে, একদিকে ব্উ আরেকদিকে দুই বাচ্চা। এই হাবিবুল্লাহ সেই হাবিবুল্লাহই, কিন্তু এই হাবিবুল্লাহ সেই হাবিবুল্লাহ নয়। তার প্রেম আমার জন্য আর একফোঁটা অবশিষ্ট নেই। আমার ইচ্ছে গুলোকে আমি নিঃশব্দে সরিয়ে রাখি।
হাবিবুল্লাহ আমাকে সেই আগের মত লাজুক হেসে বলে, ‘তোমাকে একটা কথা বলব, রাখবে?’
‘কি কথা?’ সোৎসাহে জানতে চাই। তার বুকের ভেতর আমার জন্য আগের সেই ধুকপুকুনি এখন যে আছে সে কথাই বলবে বোধ হয়।
‘জানি, তুমি পারবে, যদি চাও।’ বলে হাবিবুল্লাহ আবার সেই মিষ্টি লাজুক হাসিটি হাসে।
‘কি কথা, আগে তো শুনি।’ হৃদয় আমার চঞ্চল হয়ে ওঠে। শান্ত প্রকৃতিতে দোল লেগেছে। জলে ঢেউএর কাঁপন উঠেছে।
হাবিবুল্লাহর ঠোঁটে অপ্রস্তত হাসি। কথাটি সে শেষ পর্যন্ত বলে, যে কথাটি বলতে চায়। ‘আমাকে তুমি আমেরিকা পাঠানোর ব্যবস্থা কর।’
মুহূর্তে কাঁপন থেমে যায়। থেমে যায় সব আলোড়ন। আমার জন্য এটি এক অপার বিস্ময়। যে বিস্ময় মনকে বড় তিক্ত করে।
নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন বলি, ‘আমি? আমেরিকা পাঠাবো? কি করে পাঠাবো?’
‘তুমি পারবে। তোমার তো অনেক বিদেশে যোগাযোগ আছে। তুমি চাইলেই পারবে। এই দেশে ডাক্তারি করে কোনও টাকা পয়সা বানানো যায় না। এখন যদি আমেরিকায় যেতে পারি, তবেই ভাগ্যের পরিবর্তন হবে।’
আমি কাউকে আমেরিকা পাঠানোর ক্ষমতা রাখি না, এ কথাটি হাবিবুল্লাহকে বললেও সে মানে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার দ্বারা এখন সবকিছুই সম্ভব। আমি অসম্ভব ক্ষমতাধারী একজন কেউ।
মা হাবিবুল্লাহকে সেই আগের মত পাতে বেড়ে বেড়ে খাওয়ান। এই মার চোখে হাবিবুল্লাহ আর আমাকে নিয়ে একসময় কত স্বপ্ন ছিল। খেতে খেতে হাবিবুল্লাহ বলে, জ্ঞআমার ওয়াইফও খুব ভাল রাঁধে খালাম্মা।’
এত ওয়াইফের গল্প শুনতে মারও বোধহয় ভাল লাগে না। মা সম্ভবত জানেন, হাবিবুল্লাহর সঙ্গে আমি দেখা করতে চেয়েছি তার ওয়াইফের গল্প শোনার জন্য নয়। আমার ইচ্ছেগুলো কাউকে আমি বলিনি। কিন্তু মার নিরুত্তাপ চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়, মা আমার ইচ্ছেগুলো কখনও গোপনে পড়ে নিয়েছেন।
চলে যাওয়ার আগে হাবিবুল্লাহ বলে, ‘দেখ, তোমার এই ভাইটার জন্য কিছু করতে পারো কি না।’
প্রেমিক কি না শেষ পর্যন্ত ভাই এ নেমেছে। হা কপাল!
হাবিবুল্লাহ চলে যাওয়ার পর আমি অন্ধকার বারান্দায় একা বসে থাকি তারা ফোটা আকাশের দিকে তাকিয়ে। বড় নিঃসঙ্গ লাগে। বাড়িভর্তি মানুষ, সকলে আমার আপন, আত্মীয়, তার পরও যেন আমার মত এত একা কেউ নেই। হাবিবুল্লাহকে আমি মনে মনে ক্ষমা করে দিই। তার এই জীবনটি সেই জীবন নয়। যে জীবন যায়, সে জীবন যায়ই। বারোটি বছর চলে গেছে। অবুঝ কিশোরীর মত আমি বারো বছর আগের পুরোনো প্রেম ফিরে পেতে চেয়েছিলাম। দীর্ঘ বারো বছর। কম সময় নয়। সময় অনেকটা খুনীর মত। প্রেমকে খুন করে নিঃশব্দে চলে যায় সময়, আমাদের কারও বোঝার আগেই।
ভুল প্রেমে কেটে গেছে তিরিশ বসন্ত। যে প্রেম সত্যিকার প্রেম ছিল, তাকে অবহেলায় ছুঁড়ে দিয়েছিলাম, বুঝিনি কি হারাচ্ছি আমি। আজ বুঝি কি হারিয়েছি। আজ নিঃসঙ্গতা আমার কানে কানে বলে যায়, ‘তুমি খুব বোকা মেয়ে। তুমি আসল সোনা ছেড়ে নকল সোনা নিয়ে পড়ে ছিলে পুরো যৌবন।’ আজ আর সেই প্রেম আমি ফিরে পেতে পারি না। দেরি হয়ে গেছে। খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। কখন যে যেতে যেতে তিরিশ বছর চলে গেছে, খেয়াল করিনি। হাবিবুল্লাহ সুখে থাক বউ বাচ্চা নিয়ে। বিবাহিত পুরুষরো স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত হলে আমার ভাল লাগে। কায়সারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটি মাঝে মাঝে আমাকে দেয়। কায়সারকে বলেওছি কদিন, ‘তুই আর আসিস না আমার কাছে, হেনুকে নিয়ে সুখে থাক। অন্য কোনও মেয়ের কাছে যাওয়ার তো দরকার নেই।’ কায়সার তবুও আসে। সপ্তাহে একদিন হলেও আসে, একঘন্টার জন্য হলেও আসে। অবশ্য মাঝে মাঝে সপ্তাহ দুসপ্তাহ পার হয়ে যায়, এমনকী মাসও পার হয়, মনে হয় কায়সার বুঝি আর আসবে না, কিন্তু ঠিকই উদয় হয়। একদিন কায়সারের বউ হেনু আমাকে ফোন করে বলেছে, ‘কি করে আমার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক করেন? আপনার লজ্জা হয় না? আপনি না মেয়েদের কথা লেখেন! তবে আরেক মেয়ের সর্বনাশ করেন কেন?’ আমি ক্ষণকাল বাক্যহারা বসে ছিলাম। হেনুকে কোনও উত্তর দিতে পারিনি। এরপর শুকনো গলায় বলেছি, ‘আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন, তাকে ফেরান। তাকে বলেন যেন আমার কাছে আর না আসে।’ বড় অপরাধী লাগে নিজেকে। কিন্তু কি করে ফেরাবো আমাকে। এই সঙ্গীহীন প্রেমহীন জীবনে কায়সার যদি কোনও কোনওদিন আমাকে সামান্য সঙ্গ দেয়, আমি কী করে বাধা দেব নিজেকে সেটি গ্রহণ না করার জন্য! আমাকে সন্যাসী হতে হবে যে! এত পিপাসা রেখে কী করেই বা জল ছোঁবো না! আমি তো মানুষ, দেবী নই। অবিবাহিত কোনও পুরুষ প্রেমিক যদি পেতাম অপরাধ বোধটি যেত। কিন্তু যেতে যেতে আমার যে তিরিশ বছর চলে গেছে। সমবয়সীরা সকলেই বিবাহিত। আমার জন্য কেউ বসে নেই এই দুনিয়ায়। হাবিবুল্লাহর মত উন্মাদ প্রেমিকও বসে নেই।
আমার এখনকার বন্ধু বা শুভাকাঙ্খীর সকলে আমার চেয়ে বয়সে হয় অনেক বড়, নয় অনেক ছোট। সমবয়সী কোনও বন্ধু নেই আমার। আমার বাড়িতে যেমন অখ্যাত মানুষের আনাগোনা, তেমন বিখ্যাত মানুষের। সকলেরই সমান আদর এ বাড়িতে। মনে যদি মেলে, তবে বয়স কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বন্ধু হতে গেলে কবি বা লেখক হতে হবে, এমন কোনও নিয়ম আমার নেই। গার্মেণ্টেসএর কাঠখোট্টা ব্যবসায়ী ইয়াহিয়া খান যেমন বন্ধু, আপাদমস্তক কবি নির্মলেন্দু গুণও তেমন বন্ধু। ইয়াহিয়া খানের তবু সাহিত্যজ্ঞান কিছু আছে, মাঝে মাঝে কবিতাও লেখেন। কিন্তু খসরু সাহিত্যের ধারে কাছে নেই। শুরু থেকে শেষ অবদি তিনি ব্যবসায়ী, তিনি আমার ভাল বন্ধু। মিলনের বড় বোন মিনা স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, রুমি নামের এক ছেলের সঙ্গে দীর্ঘদিন তার প্রেম, রুমিকে বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করেছে, এ সময় তার একটি চাকরি দরকার। জীবনে কখনও চাকরি করেনি, সেই কতকাল আগে বিএ পাশ করেছে। এখন কে দেবে তাকে চাকরি। খসরুকে বললে তিনি মিনাকে তাঁর আপিসেই সেক্রেটারির একটি চাকরি দেন। স্বামীর অত্যাচারের প্রতিবাদ করে বেরিয়ে এসে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, এরকম মেয়ের সংখ্যা অনেক। অনেক মেয়ের কেবল সুযোগ নেই বলে মুখ বুজে পড়ে থাকে ভালবাসাহীন সংসারে। আমার ইচ্ছে করে একটি কর্মজীবী হোস্টেল তৈরি করতে মেয়েদের জন্য। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাবো। খসরু সাহিত্যিক নন, ডাক্তার রশীদও সাহিত্যিক নন, কিন্তু রশীদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা যে কোনও বিষয়ে আমি কথা বলতে পারি। কেবল খুব বিখ্যাত মানুষই যে জ্ঞানী হন বা উদার হন, তা নয়। এই জীবনে অনেক অখ্যাত মানুষের মহানুভবতা আর প্রশস্তচিত্ততা আমাকে অভিভূত করেছে। এত ছোট লেখক হয়েও এত তুচ্ছ প্রাণী হয়েও আমার সৌভাগ্য যে অনেক বড় বড় লেখকের সান্নিধ্য আমি পেয়েছি। এ বাড়িতে শিব নারায়ণ রায়ের মত পণ্ডিত লোকও এসে থেকেছেন। শিব নারায়ণ রায় আর অম্লান দত্তকে বক্তৃতা করার জন্য এক অনুষ্ঠানে ডেকেছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। তিনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন অম্লান দত্তকে নিয়ে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর জন্য আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা। কিছু কিছু মানুষ আছেন দেশে, যাঁদের আলোয় আমরা আলোকিত। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার দেশটিতে নক্ষত্রের মত জ্বলছেন তাঁরা। অম্লান দত্ত ছোটখাটো মানুষ, অতি সস্তা অতি মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেন, অতি সাধারণ জীবন যাপন তাঁর, হেঁটে গেলে যে কেউ ভাববে কোনও সদাগরি আপিসের ছাপোষা কেরানি বুঝি। কথা কম বলেন, কিন্তু যখন বলেন, এত সুন্দর বলেন, যে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ব ভারতীর উপাচার্য ছিলেন অম্লান দত্ত অথচ অহংকারের একটি কণাও তাঁর মধ্যে নেই। অম্লান দত্ত ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। দুজনের অনেক আগে থেকেই বন্ধুত্ব। ফেরদৌসী জাত শিল্পী। গাছের মরা ডাল শেকড় তিনি কুড়িয়ে আনেন, সেগুলোর দিকে তন্ময় তাকিয়ে থেকে থেকে আবিস্কার করেন সৌন্দর্য, শিল্প। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার চোখ সবার নেই। ফেরদৌসীর এই অসাধারণ গুণের কথা তখনও খুব বেশি কেউ জানে না। আমার বিশ্বাস, এই শিল্পটি একদিন আদর পাবে, এ দেশের একজন বড় শিল্পী হিসেবে তিনি সম্মান অর্জন করবেন। ফেরদৌসির যে গুণটি আমার সবচেয়ে ভাল লাগে, তা তাঁর সারল্য, তাঁর মুক্ত হৃদয়। তিনি কিছু লুকোতে, কিছু আড়াল করতে পছন্দ করেন না। অবলীলায় বলে যাচ্ছেন নিজের দোষের কথা, নিজের অক্ষমতার কথা, নিজের অপারগতার কথা। কজন সাধ্য রাখেন তা বলতে! ফেরদৌসীর তিন মেয়ে, রাজেশ্বরী প্রিয়রঞ্জিনী, চন্দ্রেশ্বরী প্রিয়দর্শিনী, ফুলেশ্বরী প্রিয়নন্দিনী। ফেরদৌসীও নিজের নামের সঙ্গে প্রিয়ভাষিনী যোগ করে নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তাঁর স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হই। শিবনারায়ণ রায়ের জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, হোটেল ছেড়ে দিয়ে তিনি আমার অতিথি হয়েছেন। নির্মলেন্দু গুণ আর মহাদেব সাহা এসেছিলেন শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। ‘এই যে ফতোয়া দেওয়া হল তসলিমাকে, এই যে মাথার মূল্য ঘোষণা করা হল, এর প্রতিবাদ কি কিছু করছেন আপনারা?’ শিবনারায়ণ রায় জিজ্ঞেস করলেন। নির্মলেন্দু গুণ বললেন, ‘প্রতিবাদ তো অনেক হয়েছে।’ ধমক দিয়ে উঠলেন শিবনারায়ণ, ‘অনেক হয়েছে মানে? কী হয়েছে? কতটুকু আন্দোলন হয়েছে এসবের বিরুদ্ধে? কিছুই করছেন না আপনারা। কিছুই না।’ শিবনারায়ণের সঙ্গে নির্মলেন্দু গুণের আলাপ বহু বছরের। তাঁর মেয়ে মৈত্রেয়ী রায়ের প্রেমে একসময় খুব উতলা হয়েছিলেন গুণ, মৈত্রেয়ী গুণের প্রেমে পড়েনি, গুণ শেষ পর্যন্ত নীরা লাহিড়ীর কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। ধমক খাবার পর বেশিক্ষণ বসেননি গুণ আর মহাদেব। আমি খুব অপ্রতিভ বোধ করছিলাম। ফতোয়া ঠেকানোর সাধ্য কি ওঁদের আছে! আমার দুঃসময়ে কাছে আছেন ওঁরা, এই তো আমার জন্য অনেক বেশি। ওঁরা মানুষ হিসেবে বড় বলেই সকল ঈর্ষার উর্ধে। মাঝারি কবি বা লেখকরা ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যান। সৈয়দ শামসুল হক আর হুমায়ুন আজাদের মত বড় লেখক যদি ঈর্ষা করেন, তবে মাঝারিরা করবেন না কেন! ঈর্ষা শুরু হয়েছে আমার বই যখন বেশি বিক্রি হতে শুরু হল তখন থেকে, আর আনন্দ পুরষ্কার তো ঈর্ষার আগুনকে আরও দপদপ করে জ্বালিয়ে দিল। আমার জন্মের আগে থেকে ওঁরা লিখছেন, আর কি না পুরষ্কার দেওয়া হয় আমাকে! এ কারও কারও সয়, সবার সয় না। কেবল হাতে গোনা কজন লেখক কবিই আমার সত্যিকারের বন্ধু। বন্ধু তো যে কেউ হতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের আর কজন হতে পারে! কবি রফিক আজাদকেই দেখেছি, সামনে প্রশংসা করেন, আড়ালে গাল দেন। সাহিত্য জগতে এধরনের লোকের সংখ্যাই বেশি। রফিক আজাদকে কবি হিসেবে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রচণ্ড আমুদে লোক, আড্ডা জমিয়ে রাখেন চমৎকার চমৎকার সব কথা বলে। আমি কারও থেকে দূরে সরতে চাইনি, ধীরে ধীরে বুঝেছি আমি সব কবি বা লেখকের কাছে কাঙ্খিত নই। জনপ্রিয়তা আর পুরষ্কার আমাকে অনেকটাই নিঃসঙ্গ করেছে। ফতোয়ার কারণে আমার নামটি বিদেশে জেনেছে বলে দেশের ভেতর আমি আরও বেশি নিঃসঙ্গ হয়েছি। মাঝারিরা বলছেন, ফতোয়াটির ব্যবস্থা নাকি আমি নিজেই করেছি, যেন নাম হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, আসলে কি ওঁরা আমাকে ঈর্ষা করেন! নাকি এ নিতান্তই আমার আত্মাভিমান! নিজেকে আমি এত বড় ভাবছি যে মনে হচ্ছে আমি যেন ঈর্ষার বস্তু হয়ে গেছি। অন্য কিছুও তো হতে পারে, সম্ভবত আমি ভাল লেখক নই, ভাল কবি নই, সে কারণেই আমার নামটি কালো কালিতে ঢেকে দিয়েছেন ওঁরা। ছোট লেখক যদি বড় পুরস্কার হাতিয়ে নিতে পারে, সন্দেহ হবে না কেন ওঁদের! ওঁদের চোখ দিয়েও নিজেকে দেখি আমি, যদি বাজারে গুঞ্জন শোনা যায় যে আমি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ঘুস নিয়েছি একটি বই লিখে, আর সেই টাকায় নিজের সুখের জন্য বাড়ি গাড়ি কিনেছি, তবে কেন ওঁরা কুঞ্চিত চোখে কুপিত দৃষ্টি ছুঁড়বেন না! আমাকে কুটিল, কূলটা, কুচরিত্র বলেই তো মনে হবে। আমাকে ঘৃণা না করার, ভাবি, কোনও কারণ নেই।
আমার ইশকুল বা কলেজ জীবনের কোনও বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। ঝুনু খালার মুখে শুনেছি, আমার ইশকুলের বান্ধবী সারা এখন ভিখারুন্নেসা ইশকুলের বাংলার শিক্ষিকা। শুনে আমি উত্তেজিত সারার সঙ্গে দেখা করার জন্য। সারা একদিন আসে আমার বাড়িতে। আমরা দুজন মুখোমুখি বসি। কথা হয়। কিন্তু সে কথায় প্রাণ নেই। এই সারার সঙ্গে ছোটবেলার কত মধুর দিন কেটেছে আমার, আজ সারার সঙ্গে কথা বলার মত কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর বন্ধুরা কে কোথায় আছে জানতে চাওয়া, স্বামী কি করে, বাচ্চাদের বয়স কত এসবের পর আমরা দুজন চুপচাপ বসে থাকি। বিদ্যাময়ী ইশকুলের বান্ধবী পাপড়ি আমার শান্তিবাগের বাড়িতে একদিন এসেছিল, ওর সঙ্গেও কথা খুঁজে পাইনি বেশি। জীবন যাপনের পার্থক্য বড় বেশি দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। আমার কোনও স্বামী সন্তান নেই। সবাই এখন ঘর সংসার করছে। সবারই চাকরি বাকরি আছে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত। এখন পুরোনো বান্ধবীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ওঠা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না, বিশেষ করে সে বান্ধবী যদি একা হয়। ভয় তো খানিকটা কাজ করেই, স্বামী যদি আবার প্রেমে পড়ে যায় বান্ধবীটির। তার চেয়ে বিবাহিতাদের বিবাহিতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা স্বস্তিকর। আমার ডাক্তার বন্ধু বা বান্ধবীরা এখন কে কোথায় আছে, জানি না। ঢাকা শহরে নিশ্চয়ই অনেকে আছে, কিন্তু কারও সঙ্গেই আর দেখা হয় না। নাসিমুল যখন মিটফোর্ডে কাজ করত, দেখা হয়েছে কদিন। ও জাপানে যাবার চেষ্টা করছিল তখন। সবাই কেমন দূরে চলে গেছে। অথচ সেই দিনগুলি মনে হয় এত কাছে, যেন হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যাবে। যেন বন্ধুরা আবার সব একসঙ্গে হব। কোথায়! দিন তো কেবল চলেই যাচ্ছে। আমরা তো পরস্পরকে কেবল হারিয়েই ফেলছি। তিন বছর আগে হঠাৎ একদিন বইমেলায় শাফিনাজ এসেছিল হন্তদন্ত হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে, চেম্বার থেকে খানিকক্ষণের জন্য ছুটি নিয়ে ছুটে এসেছিল। বিদ্যাপ্রকাশের দোকানে ঢুকেই আমাকে বলল, কেমন আছ, তোমার জন্য চিন্তা হয়, সাবধানে থেকো কেবল এটুকুই বলার সময় ছিল ওর। রোগী বসে আছে, ফিরে যেতে হবে। শাফিনাজ, কী ঘনিষ্ঠই না ছিল আমার। ঢাকা শহরেই দুজন বাস করি, অথচ বছর চলে যায়, বয়স চলে যায়, দেখা হয় না। পিজি হাসপাতালে একবার শিপ্রার সঙ্গে গিয়েছিলাম, হালিদার সঙ্গে দেখা হয়েছে। খুব অল্প সময় কথা হয়েছে। হালিদা তখনও বিয়ে করেনি, বলেছে বিয়ে টিয়ে ও আর করছে না। এই একজনই বিয়ে না করা বান্ধবী আছে। শিপ্রা, খসরু একদিন জানালেন, রাজশাহী চলে গেছে। ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে যদি কোনও বড় হাসপাতালে চাকরি করা যায়, কোনও না কোনও সূত্রে যোগাযোগ হয়ত হত। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বিচ্ছিত হয়ে গেলে সেই যোগাযোগটিও আর থাকে না। একদিন আমার এক ইশকুলের বান্ধবী এসেছিল শান্তিবাগের বাড়িতে, সে মিটফোর্ড হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে। আমাকে হাসপাতালে প্রতিদিনই দেখেছে, কিন্তু লজ্জায় পরিচয় দিতে পারেনি। আমি ডাক্তার, সে নার্স, তাই নাকি তার লজ্জা হয়েছে পরিচয় দিতে। এত অন্যরকম হয়ে গেছে লাকি, সেই আগের গাল ফোলা মুখটি আর নেই, চোখ বসা, গাল বসা মেয়েটি যে সেই লাকি, পরিচয়ের পরও আমার চিনতে কষ্ট হয়েছে। মাঝে মাঝে ভাবি, আমি দূরে চলে গেছি, নাকি ওরা দূরে চলে গেছে! নাকি সময় আমাদের দূরে সরিয়েছে! নাকি জীবনই এমন, পুরোনো ফেলে নতুনের দিকে যেতে চায় কেবল! পুরোনো দিনের কথা জানালায় বসে ভাবতে ভাল লাগে, দিনগুলো আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। যখন কল্পনা করি সেই জীবনে ফেরার, তখন এই বয়সে সেই জীবনে যাওয়ার কল্পনা করি না, মনে মনে আসলে সেই বয়সী, সেই পুরোনো পরিবেশের মানুষটি আমি যাই সেই জীবনে, সেই পুরোনো মানুষটিকে পুরোনো জীবনে ফেরানো আর এখন পুরোনোকে নতুন জীবনের মধ্যিখানে সত্যিকার দাঁড় করানো দুটো দু জিনিস। মেলে না। অবকাশ আমার কত আপন, অথচ এখন অবকাশে গেলে বেশিক্ষণ কাটাতে ইচ্ছে করে না, কী যেন বড় বড় নেই নেই লাগে। কী নেই! আমার শৈশব কৈশোরটি আমার ভেতরে আর নেই! নাকি আগের মানুষগুলো আর আগের মত নেই! বদলে গেছে। সবকিছুই বদলে যাচ্ছে। স্বীকার করতেই হয় যে আজ যে দিন চলে যাচ্ছে, সে দিন চলে যাচ্ছেই। আগামীকালের দিনটি নতুন একটি দিন। আজ যা হারাচ্ছি, কাল তা ফিরে পাবো না। আমরা খুব দ্রুত ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছি, এত দ্রুত, যেন দৌড়োচ্ছি। আমরা বড় হয়ে যাচ্ছি, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, আমাদের সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, ভাবলে বুকের মধ্যে চিনচিন একটি ব্যথা হয়, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়, জীবন এত ছোট কেন! কাকে বলব, সকলেই তো জানে জীবন খুব ছোট। সম্ভবত মিনু জানে না, মিনুর কাছে জীবন খুব দীর্ঘ বড় দীর্ঘ বলে মনে হয়, যেন ফুরোচ্ছে না। একটিই জীবন আমাদের, কেউ এটিকে হেলায় ফেলায় নষ্ট করে, কেউ এটিকে দুর্বিসহ বলে মনে করে, কারও কাছে জীবন বড় অমূল্য সম্পদ। এক আমার কাছেই জীবনকে মনে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন, কখনও এটি সুন্দর, কখনও কুৎসিত, কখনও সয়, কখনও নয়, কখনও আবার এর রূপ রস গন্ধে এত বিভোর হই যে আঁকড়ে ধরি যেন কোনওদিন পালিয়ে না যায়।
ঢোলের বাজনা শুনছি। রাস্তায় জমজমাট পয়লা বৈশাখের শোভাযাত্রা। ছেলেরা ধুতি পরে ঢোল বাজাচ্ছে, মেয়েরা আটপৌরে শাড়ি পরে কলসি কাখে নাচছে। রঙিন কাগজে বানানো বিশাল বিশাল হাতি ঘোড়া বাঘ ভালুক নিয়ে হাঁটছে মানুষ। রূপকথার চরিত্রদের মুখোশ পরেছে অনেকে। ছায়ানট সকাল থেকে বসে গেছে রমনার বটমূলে। চারদিকে গানের উৎসব হচ্ছে। সমবেত কণ্ঠে বাঁধ ভেঙে দাও এর সুর, জীর্ণ পুরাতন ছূঁড়ে ফেলে নতুনকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। পুরো ঢাকার মানুষ জড়ো হয়েছে রমনায়, রমনার আশে পাশে। নকশি কাঁথা পেতে বসেছে ঘাসে, তালপাখায় বাতাস করছে। মুড়িমুড়কি খাচ্ছে। সোহরওয়ার্দি উদ্যানে ফকির আলমগীর গাইছেন মানুষের মুক্তির গান। আগে অর্ধেক রাত পর্যন্ত ফকির আলমগীরের মঞ্চ বানানোর কাজ দেখতাম, গানের আড্ডায় কেটে যেত পয়লা বৈশাখের আগের রাতটি। প্রতি পয়লা বৈশাখে হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে আমিও ছিলাম। ভোর বেলা থেকে শুরু করে মধ্য রাত পর্যন্ত উৎসবে, আনন্দে। আমার তো বছরে দুটো দিনই আছে উৎসবে মাতার। একুশে ফেব্রুয়ারি আর পয়লা বৈশাখ। আমার ঈদ নেই, শবে বরাত নেই, শবে কদর নেই, ফাতেহা এ দোয়াজদহম, ফাতেহা এ ইয়াজদহম, মিলাদুন্নবি নেই। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে কোনও ধর্মীয় উৎসবে আমি জড়িত হই না। আমার কেবল ছিল বাংলা আর বাঙালির উৎসব। আজ সবারই অধিকার আছে, কেবল আমারই নেই উৎসবের একজন হওয়ার, মাঠে ময়দানে কোথাও গিয়ে গান শোনার অধিকার আমার নেই। রমনায় আজ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে সানজিদা খাতুনের ছায়ানট। মাঠে মাঠে আজ মেলা বসেছে। চারদিকে কুটিরশিল্পের মেলা, বাংলা বইয়ের মেলা, গানের মেলা, নৃত্যমেলা, উৎসব উৎসব গন্ধ ভেসে আসছে চারদিক থেকে। কেবল আমিই, আমিই একা ঘরে, জীর্ণ পুরাতন আমি, বসে আছি একা একা, নতুনকে বরণ করার অধিকার আমার নেই। বিষণ্নতা আমাকে বিবশ করে রাখে।
বিকেলে মা আমার ঘরে উঁকি দিয়ে ঠোঁট উল্টো বললেন, ‘এইবারের পয়লা বৈশাখের মেলা নাকি জমে নাই।’
‘কে কইল তোমারে?’
‘পাশের বাসার চুমকির মা কইল। গেছিল মেলায়। লোকই নাকি নাই।’
খানিক বাদেই মা প্রসন্ন মুখে আমার জন্য ভাজা-মুড়ি আর আদা-চা নিয়ে ঘরে ঢোকেন।
‘ছায়ানটের গান ত হইতাছে, কিছু কইছে?’ আমি মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, উৎসুক জানার জন্য।
মা আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে ‘এই বিশ্রী গরমের মধ্যে গান শুনতে বাইরে কে যায়? ঘরে বইসা গান শুনাই ভাল’ বলে দ্রুত বেরিয়ে যান। মাকে কেমন অস্থির দেখায়। মনে হয় লুকোচ্ছেন কিছু। মা কি আমার মেলায় যেতে না পারার কষ্ট কমাতে মিথ্যে বলছেন! পাশের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চুমকির মাকে ডেকে একবার আমার জানতে ইচ্ছে হয় মেলা সত্যিই জমেনি কি না। মার রেখে যাওয়া ভাজা মুড়ি চিবোতে চিবোতে চায়ে চুমুক দিয়ে মার চালিয়ে দেওয়া গান জ্ঞচারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি….’ শুনতে শুনতে মনে মনে বলি, না থাক, মেলা হয়ত সত্যিই জমেনি।