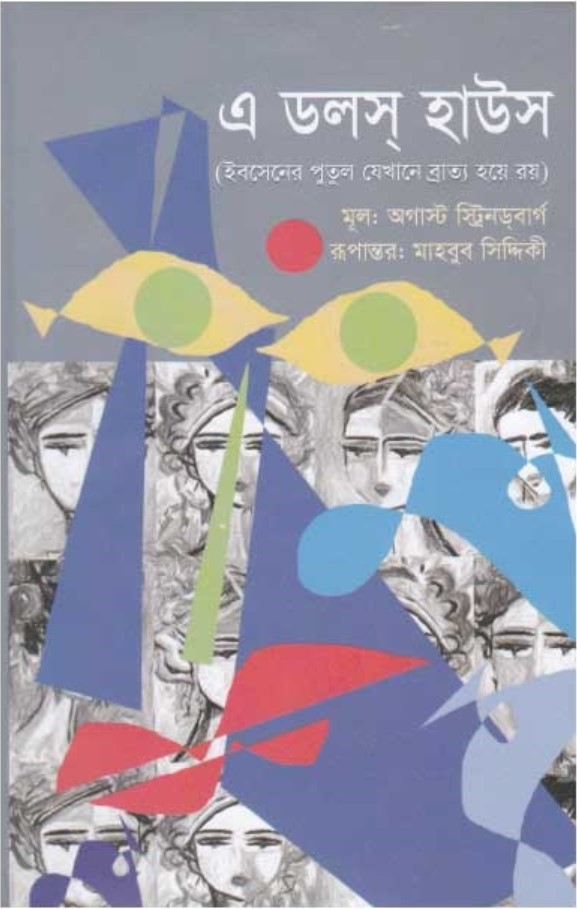- বইয়ের নামঃ এ ডলস্ হাউস
- লেখকের নামঃ অগাস্ট স্ট্রিনডবার্গ
- প্রকাশনাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ
- বিভাগসমূহঃ নাটকের বই, অনুবাদ বই
অপ্রাকৃতিক নির্বাচন
‘দ্য স্লেভস অব লাইফ’ বইটা পড়ে আমাদের ব্যারন [অভিজাতদের মধ্যে সর্বনিম্ন উপাধি] সাহেব প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছেন। বইটাতে তিনি পড়েছেন, “অভিজাত শ্রেণির শিশুরা হয়ত মারাই যেত যদি নীচু শ্রেণির কোন মা তাদেরকে বুকের দুধ পান না করাত।” ব্যারন সাহেব ডারউইনও পড়েছেন। সারমর্ম হিসেবে তাঁর মনে হয়েছে “প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অভিজাত শ্রেণির শিশুরা ‘মানুষ’ প্রজাতির আরও উন্নত প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভূত হয়।” কিন্তু ‘বংশগতি বিদ্যা’ পড়ে তিনি তাঁর অনাগত সন্তানের জন্য নার্স ঠিক করার ব্যাপারে বেশ অনিচ্ছুক হয়ে উঠেছেন–নীচু শ্রেণির কোন নার্সের দুধ পান করলে অভিজাত শ্রেণির শিশুর রক্তে নীচু ধ্যানধারণা ঢুকে যেতে পারে, এই ভয়ে। সবকিছু মিলে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর স্ত্রী নিজেই সন্তানের দেখাশোনা করবেন, আর কোন কারণে সেটা সম্ভব না হলে, সন্তানকে বোতলের দুধ পান করানো হবে। অবশ্য, গরুর দুধেও আপত্তি নেই; কারণ গরুগুলোকে তো তিনিই খাওয়াচ্ছেন, তিনি খাইয়ে বাঁচিয়ে না রাখলে তো বাছুরগুলো জন্মই নিতে পারত না! সুতরাং, গরুর দুধও গ্রহণযোগ্য।
যথাসময়ে সন্তানের জন্ম হলো–পুত্রসন্তান। ব্যারন সাহেব স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত না-হওয়া পর্যন্ত বেশ চিন্তিত ছিলেন। কারণ, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজের তেমন কোন সম্পত্তি না থাকলেও, তাঁর স্ত্রী অঢেল সম্পদের মালিক। এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী, তাদের কোন সন্তানাদি না-হওয়া পর্যন্ত, এই সম্পত্তি তিনি দাবি করতে পারবেন না। অতএব, সন্তান হওয়াতে তাঁর আনন্দ সীমাহীন, এবং তা যথেষ্ট যৌক্তিকও বটে! যাহোক, শিশুটিকে দেখে আপাত দৃষ্টিতে নিখুঁত বলেই মনে হচ্ছিল। ওর মোমের মত ত্বকের নীচের নীলাভ শিরা-উপশিরাগুলো চকচক করছিল। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায় শিশুর শরীরে রক্তের অভাব। কারণটা অবশ্য ওই রক্তেই নিহিত! ওর মা দেখতে পরীর মত; সেরা-সেরা খাবার খাইয়ে, চারপাশের যাবতীয় খারাপ কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখে, তাঁকে বড় করা হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও মুখের ফ্যাকাসে ভাবই বলে দিত। তিনি অভিজাত গোত্রভুক্ত। এবং সঙ্গত কারণেই, তাঁর শরীরে পুষ্টির ঘাটতি ছিল। এই ঘাটতি এখন তাঁর সন্তানের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছে। যাহোক, ব্যারনের স্ত্রী নিজেই সন্তানের দেখাশোনা করতে লাগলেন। ফলে, সন্তান পালনের জন্য নীচু জাতের কোন মেয়ের কাছে আর ঋণী থাকতে হলো না। ধুর! কে বলেছে নীচু জাতের মায়েরা দুধ না-খাওয়ালে অভিজাত ঘরের শিশুরা বাঁচে না? সব ভুয়া কথা!।
ইদানিং, রাতবিরেতে শিশুর চিৎকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য, সব শিশুই চিৎকার করে, ওতে খারাপ কিছু বোঝায় না। কিন্তু এখানে বোঝালো। ধীরে ধীরে শিশুর ওজন কমতে থাকল। ভীষণ শুকিয়ে গেল। অগত্যা ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার এসে শিশুর বাবার সঙ্গে আলাদা বসে কথা বললেন–“যদি আপনার স্ত্রী-ই শিশুকে খাওয়ানোর দায়িত্বে থাকেন, তাহলে নির্ঘাৎ শিশুটি মারা যাবে। কারণ প্রথমত, ব্যারনের স্ত্রী ছিলেন অস্বাভাবিক শুকনো; এবং দ্বিতীয়ত, শিশুকে খাওয়ানোর মত পর্যাপ্ত খাবার তাঁর শরীরে মজুদ ছিল না। ব্যারন সাহেব পড়লেন বিরাট দুর্ভাবনায়। শিশুর কতটুকু দুধ প্রয়োজন, আর কতটা সে পাচ্ছে, তা নিয়ে হিসেবে (রীতিমত গাণিতিক হিসাব!) বসে গেলেন। ফলাফল বেরোলো এই যে, শিশুকে খাওয়ানোর পদ্ধতিগত পরিবর্তন না-আনলে এর মৃত্যু ঠেকানো অসম্ভব।
কী করা যায়?
আর যা-ই হোক, মারা তো যেতে দেয়া যায় না।
“বোতল নাকি নার্স?” দ্বিতীয়টির তো প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে, বোতলেই সই! যদিও ডাক্তারের পছন্দ ছিল দ্বিতীয়টি।
হল্যান্ডের সবচাইতে উন্নত জাতের গরুটিকে আলাদা করা হলো। বলা বাহুল্য, এ গরু জেলার সেরা গরু হিসেবে সোনার মেডেলপ্রাপ্ত। সবচেয়ে উন্নত জাতের খাবার খাওয়ানো হতে লাগলো সেটিকে। ডাক্তার এসে দুধ পরীক্ষা করে গেলেন–“সবকিছু একদম ঠিকঠাক।”
বাহ্! কী সহজ সমাধান! ভাবতেই অবাক লাগছে, আগে কেন মাথায় আসেনি!
অতএব, নার্সের ঝামেলা চুকলো। বাচ্চার জন্য নার্স রাখা মানে তো এক স্বৈরাচারীকে ঘরে আনা! সে যেভাবে যা বলবে তা-ই শুনতে হবে। কোথাকার কোন অকর্মার ঢেঁকি! তাকে খাইয়ে-পরিয়ে মোটা বানাতে হবে। আর, তার যদি কোন সংক্রামক রোগবালাই থাকে তাহলে তো কথাই নেই।
কিন্তু বিধি বাম! শিশুর চিৎকার থামছেই না। সেই সাথে ওজন হ্রাসের চলমানতা। দিন গড়িয়ে রাত, রাত গড়িয়ে দিন–চিৎকার বিরামহীন। বোঝাই যাচ্ছে, শিশু পেটের অসুখে ভুগছে। তবে উপায়?
নতুন গরু কেনা হলো। নতুন করে দুগ্ধ বিশ্লেষণ। এবারে, দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে গুণে-মানে কিছুটা পরিবর্তন করা হলেও, শিশুর চিৎকার অপরিবর্তনীয়।
“নার্স নিয়োগ ব্যতীত আরোগ্য অসম্ভব”, ডাক্তারের স্পষ্ট বক্তব্য।
–“ওহ্! এছাড়া কি আর কোনও উপায় নেই? একজন এসে অন্যজনের সন্তানের দায়িত্ব নেবে এটাতো প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইয়ে, মানে, তাছাড়া, বংশগতির কী হবে? এই জাতীয় নানান কথায় ব্যারন সাহেব যখন প্রকৃতিবিরুদ্ধতা নিয়ে বিরাট ফিরিস্তি দিতে বসেছেন, তখন ডাক্তার তাঁকে থামালেন–“প্রকৃতিকে যদি তার নিজের মত করে চলতে দেয়া হত, তাহলে সমাজে অভিজাত সম্প্রদায় বলে কিছু থাকত না, তাদের সহায়-সম্পত্তি ধূলায় লুটাত। কারণ, অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টিই হয়েছে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে।”
হতোদ্যম ব্যারনের যেন জাত গেল! প্রমাণিত হলো, তাঁর স্ত্রী নিজের গর্ভের ফসলকে টিকিয়ে রাখতে অক্ষম। অতএব, হয় তাকে অন্য স্ত্রীলোকের থেকে দুধ কিনতে হবে, নয়তো চুরি-ডাকাতি করে আনতে হবে! ব্যারনের বংশ চুরির সম্পত্তিতে টিকে থাকবে? এ-ও ছিল ঘটে!
–কিন্তু পয়সা দিয়ে দুধ কিনলে তাকে কি চুরি-ডাকাতি বলা যায়?
–অবশ্যই বলা যায়। কারণ, যে টাকা দিয়ে এটা কেনা হল, সেটা তো। কারও না কারো পরিশ্রমের ফসল। কার পরিশ্রম? অবশ্যই সাধারণ জনগণের পরিশ্রম; কেননা, অভিজাত সম্প্রদায় তো আর যা-ই করুক পরিশ্রম করে না।
হুমম! ডাক্তার ব্যাটা তাহলে সমাজতান্ত্রিক!
অবশ্য, ডারউইনের অনুসারীও হতে পারে–কথার মধ্যে কেমন একটা অন্যরকম গন্ধ আছে! তবে, যে যা-ই বলুক না কেন, ডাক্তার সাহেব নিজে এগুলোর কোনটাতেই গা করেন না। এসব তাত্ত্বিকতা নিয়ে মাথা ঘামানোর মত যথেষ্ট অবসর তাঁর নেই।
কিন্তু “পয়সা দিয়ে কেনা মানে ডাকাতি করা “ এ বড় শক্ত কথা। এক্ষেত্রে বিধান কী বলে? “যদি ঐ টাকা দিয়ে কেনা হয়, যে টাকা পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি!” সংশয়ী ব্যারনের প্যাচালো জিজ্ঞাসা।
“অর্থাৎ, কায়িক পরিশ্রমের কথা বলছেন তো?” ডাক্তার সাহেবের সরলীকরণ।
“ঠিক তাই।” আনন্দে হাতে কিল দিলেন ব্যারন।
কিন্তু এভাবে চিন্তা করলে তো দেখা যায় ডাক্তারও ডাকাতি করে!
হুমম! ঘটনাতো তা-ই দাঁড়াচ্ছে।
তবে, যা-ই হোক না কেন, সত্য স্বীকারে ব্যারন পিছপা হবেন না, এমনই তাঁর প্রতিজ্ঞা। কিন্তু গুরুগম্ভীর আলোচনার এ পর্যায়ে খানিক বিঘ্ন ঘটলো। সঠিক সিদ্ধান্ত চেয়ে ব্যারন সাহেব এক খ্যাতনামা প্রফেসরের কাছে। লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলে পাঠিয়েছেন, “স্পষ্টত ব্যারন একজন খুনী; কারণ, তাঁর উচিত ছিল আরও আগেই নার্স নিয়োগ করা।”
তবে আর কী!
এবার তাহলে বউকে রাজি করানোর পালা। ব্যারনকে তাঁর আগের অবস্থান থেকে সরে আসতে হল। পূর্ববর্তী সকল যুক্তি ত্যাগ করে একটাই অবস্থান তৈরি হল–‘সন্তানের প্রতি ভালোবাসা’ (যদিও এখানে উত্তরাধিকার আইনের প্রভাব কতটা, তা বলা যাচ্ছে না!)।
কিন্তু মূল সমস্যা তো মূলেই রইল! নার্স পাওয়া যাবে কোথায়? শহরে খোঁজা উচিত হবে না, কারণ শহুরে মানুষের নীতি-নৈতিকতা বলে কিছু নেই। নাহ্! গ্রাম থেকেই আনতে হবে। তবে, একটা ব্যাপারে বউয়ের ঘোরতর আপত্তি আছে, “অবিবাহিতা কোন নার্স হলে চলবে না।” অবিবাহিতা মেয়ে অথচ তার বাচ্চা আছে, এমন মেয়েতো দুশ্চরিত্রা। আর, এমন কারও বুকের দুধ পান করলে তাঁর ছেলের স্বভাবেও খারাপ কিছু ঢুকে যেতে পারে!
অতএব, এ-ব্যাপারেও ডাক্তারকে হস্তক্ষেপ করতে হলো–“যেসব নার্স অন্যের বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায়, তারা সবাই-ই অবিবাহিতা; কারণ, একজন সামর্থ্যবান স্বামী কখনোই তার স্ত্রীকে অন্যের বাড়ি গিয়ে, অন্যের সন্তানকে স্তন্যপান করাতে দেবে না। বরং চাইবে, স্ত্রী-সন্তান তার নিজের কাছেই থাকুক।
ব্যারনের কপালে চিন্তার ভাজ, এবং অতঃপর… ইয়েস! আইডিয়া পাওয়া গেছে। তারা যদি কোন গরীব ঘরের মেয়েকে নিজেদের পরিচিত কোন মজুরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়?
তবুও তো অন্তত নয় মাস অপেক্ষা করতে হবে।
তাহলে ধরা যাক, বাচ্চা আছে এমন কোন মেয়েকে তারা বিয়ে দিয়ে দিল?
হুম! সেটা অবশ্য মন্দ নয়!
তিন মাসের একটা বাচ্চা আছে এমন এক মেয়েকে ব্যারন চিনতেন। বেশ গভীরভাবেই চিনতেন বলা যায়; কারণ, তিন বছর সম্পর্কের পর ‘ডাক্তারের নির্দেশে তিনি মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অগত্যা, সেই মেয়েটির কাছেই প্রস্তাব নিয়ে গেলেন–অ্যানডার্স নামের এক মজুরকে যদি সে বিয়ে করতে রাজি হয়, তবে তাকে আস্ত একটা ফার্ম দিয়ে দেয়া হবে। মেয়েটা চিন্তা করে দেখল–একা একা লাঞ্ছনা সহ্য করার চেয়ে এমন লোভনীয় প্রস্তাবে রাজি হওয়াটাই বুদ্ধিমতির কাজ হবে। সুতরাং, পরের রোববার বিয়ের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হল। এবার, বউকে রেখে পরবর্তী দুমাসের জন্য অ্যানডার্সকে তার গ্রামের বাড়ি চলে যেতে হবে।
একটা বিষয় নিয়ে ব্যারন সাহেব মনে মনে হিংসায় জ্বলে মরছিলেন ‘নার্সের বাচ্চা ছেলেটা। বড়-সড়, শক্ত-পোক্ত একটা বাচ্চা। যদিও দেখতে ভালো নয়, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় এ জিনিস অনেকদিন টিকবে! বেঁচে থাকার জন্যই এর জন্ম হয়েছে, স্বপ্নপূরণের জন্য নয়। তবে, ব্যারনের ছেলে আর নার্সের ছেলে তো এক বাড়িতে, এক মায়ের দুধ খেতে পারে না, তাই না? তাই, কায়দা করে নার্সের ছেলেটিকে এতিমখানায় পাঠিয়ে দেয়া হল। প্রথমদিকে অ্যানা (নার্স) ভীষণ কান্নাকাটি করল। কিন্তু এ বাড়ির এলাহী খানাদানা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার কান্না থামাতে সমর্থ হল (তার খাবার আসত ঘরের ভেতর ডাইনিং রুম থেকে; আর, মদ তো যখন যেমন খুশি চলতই)। বাড়ির বাইরে যাবার ব্যাপারেও তার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। মস্ত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে, গার্ড সাথে নিয়ে সে বেড়াতে বের হত। অবসরে আরব্য রজনীর গল্প পড়ত। জীবনে এত সুখ কখনও সে কল্পনাও করেনি।
দুমাস পর আবার অ্যানডার্সের দেখা মিলল। এ অব্দি সে ফার্মেই ছিল। এতদিন খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া কিছুই করেনি। এবার আবদার করল অ্যানাকে কাছে পাবার জন্য। “মানে, অ্যানাকে কি অন্তত মাঝে মাঝে দু’ একদিনের জন্যও পাঠানো যায় না?”
“অসম্ভব!” ব্যারনের বউয়ের বজ্রনিনাদ। “কোনও রকম জারিজুরি চলবে না।”
এবার, অ্যানাকে রোগে ধরল। ক্রমাগত সে শুকাতে থাকল, সেই তালে ব্যারনের ছেলের ক্রমাগত কান্না। দৃশ্যপটে আবারও ডাক্তার।
–ওকে কিছুদিন স্বামীর সাথে থাকতে দিন।
–কিন্তু বাচ্চার সমস্যা হবে যে!
–না-না, অল্প কয়েকদিনে তেমন কিছু হবে না।
কিন্তু অ্যানডার্সটাকে আগে তলিয়ে দেখতে হবে। কোন বদ মতলব আছে কি না জানা দরকার! অ্যানডার্স গড়িমসি করতে থাকল… এবং…, ‘তলিয়ে দেখা সম্পন্ন হল। প্রক্রিয়াটি অবশ্য খুব জটিল কিছু না–কতগুলো ভেড়া পেয়েই অ্যানডার্স সন্তুষ্ট। তার গড়িমসি বন্ধ হল। বন্ধ হল ব্যারনপুত্রের কান্নাও।
কিছুদিন পর, এতিমখানা থেকে এক দুঃসংবাদ এলো–অ্যানার ছেলেটা ডিপথেরিয়ায় মারা গেছে।
অ্যানা যেন কেমন হয়ে গেল। সব সময় মনমরা হয়ে থাকে, কাজেকর্মে সাড়া পাওয়া যায় না, সব কিছুর প্রতি কেমন একটা উদাস-উদাস ভাব। ফলাফল যা হবার তাই হল–আবারও ব্যারনপুত্রের ক্রন্দনরোল। এবার আর কোন মধ্যবর্তী পন্থা চিন্তা করা হল না, অ্যানাকে চাকরি হারাতে হল। ওকে অ্যানডার্সের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নতুন নার্স নিয়োগ দেয়া হল।
শেষ পর্যন্ত, বউ ফিরে পেয়ে অ্যানডার্সততা আহ্লাদে আটখানা। অবশ্য, এ আহ্লাদ আর্তনাদে পরিণত হতেও খুব বেশি সময় নিল না–অ্যানা বড় খরুচে হয়ে গেছে। ব্রাজিলিয়ান কফি না-হলে তার মুখে রুচে না, প্রতিদিন একই খাবার পছন্দ হয় না। সপ্তাহে ছয়দিন মাছ খেতে-খেতে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে, ফার্মে কাজ করতে ভীষণ কষ্ট হয়। ফলে, ফার্মের উৎপাদন কমে গেল। লোকসান সামলাতে না-পেরে, বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই অ্যানডার্সকে ফার্ম ছাড়তে হল। এইবেলা ব্যারন বেশ দয়া দেখালেন ওদেরকে ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতে দিলেন।
*** *** ***
অ্যানা এখন ব্যারনের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। হামেশাই ব্যারনপুত্রের সঙ্গে তার দেখা হয়। অ্যানাকে সে চিনতে পারে না। অবশ্য চিনতে চায় না বলাটাই যথার্থ হবে। এমনই তো হবার কথা ছিল–ব্যারনপুত্রকে নিজের বুকের দুধ খাইয়েছে সে, তাকে বাঁচাতে গিয়ে পেটের ছেলেকে বলি দিয়েছে; আজ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ (!) ব্যারনপুত্র তাকে চিনবে না সেটাই তো স্বাভাবিক, সেটাই তো আভিজাত্য। যাহোক, অ্যানা কিন্তু যথেষ্ট উৎপাদনশীল ছিল। পরবর্তীতে তার আরও অনেকগুলো ছেলেপুলে হয়েছে, যারা ক্ষেতে-খামারে মজুর হিসেবে, কিংবা কুলি হিসেবে রেলওয়েতে কাজ করে। একজন আবার দাগী আসামি, এখন জেল খাটছে।
ব্যারন সাহেব এখন পুত্রের বিয়ের দিন গুনছেন। নাতি-নাতনীর মুখ দেখতে আকুল তিনি। পুত্র অবশ্য খুব একটা শক্তপোক্ত হয়নি। যে-কারণে ব্যারন সাহেব মাঝে মাঝেই অন্যরকম ভাবেন–সেই এতিমখানায় মারা যাওয়া পুত্রটি যদি আজ তাঁর উত্তরাধিকারী হত, তবে তিনি অনেকটাই নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন। ইত্যবসরে, দ্বিতীয়বারের মত ‘দ্য স্লেভস অব লাইফ’ পড়ে ব্যারন সাহেব স্বীকার করতে বাধ্য হলেন–“উঁচু শ্রেণি টিকেই থাকে নীচু শ্রেণির দয়ার ওপর।” ডারউইনের পুনঃপঠনে তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না–“প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যাপারটা সবসময়ই অলঙ্ঘনীয়। যে যা-ই বলুক না কেন এ সত্য চিরদিন ধ্রুব হয়েই থাকবে।”
এ ডলস্ হাউস
বিয়ের বয়স প্রায় ছ’বছর হয়েছে। কিন্তু এখনও দেখলে প্রেমিক-প্রেমিকাই মনে হয়। স্বামী জাহাজের ক্যাপ্টেন। প্রত্যেক গ্রীষ্মে দীর্ঘভ্রমণে বের হতে হয়। ফলে বেশ কিছুদিন বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। এতে অবশ্য এক রকম ভালোই হয়েছিল। কারণ, শীতকালে নিজেদের মধ্যে একটু-আধটু মন কষাকষি হলেও কিছু দিনের অনুপস্থিতি শেষে দুজনের প্রেম একেবারে নতুন করে শুরু হত!
স্বামী জাহাজে থাকাকালীন নিয়মিত স্ত্রীকে চিঠি লেখে, আর পাশ দিয়ে কোন জাহাজ যেতে দেখামাত্র চিৎকার করে বলে–“আমার চিঠিটা নিয়ে যাও, প্লিজ।” এমনি করে কতভাবে, কত চিঠি যে সে পাঠায় তার ইয়াত্তা নেই। অবশেষে একদিন যখন দূর থেকে স্টকহোমের বন্দর দেখা যায়, তখন ক্যাপ্টেনের আর তর সয় না। কীভাবে, কত দ্রুত স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। শেষমেশ একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে যায়–স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করে দেয়, যেন সে আগে থেকেই বন্দরের কাছে দালাছড়া শহরের কোন একটা হোটেলে এসে ওঠে।
জাহাজ বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছালে হোটেলের বারান্দায় একটা ছোট্ট নীল স্কার্ফ উড়তে দেখা যায়। সেটা দেখেই স্ত্রীর উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয় স্বামী। “আহ! জগতে এর চেয়ে আনন্দ বুঝি আর হয় না!” কিন্তু সময় যে যেতে চায় না! বন্দরে ভেড়ার পরও জাহাজে এত কাজ থাকে যে মুক্তি পেতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। জাহাজ থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে করে আসার সময়ও সে বার-বার মুখ বের করে অতি কষ্টে স্ত্রীর মুখটা দেখার চেষ্টা। করে। এবং … এবং, অবশেষে তাদের সাক্ষাৎ! তারা যে কী বলবে, কী করবে, তার যেন কোন কূল-কিনারা পায় না। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্বামী ভাবে, “ও ঠিক আগের মতই আছে। সেই হাসি, সেই সৌন্দর্য, সেই উফুল্লতা, সবই সেই আগের মত: ঠিক যেমন আগেরবার দেখেছিলাম।” স্ত্রীর মনেও একই ভাবনা। এভাবেই কিছুক্ষণ ঘোরের মধ্যে কাটে তাদের। এরপর আস্তে আস্তে অস্থিরতা খানিক কমে, সবকিছু একটু স্বাভাবিক হয়। এবার খোঁজ-খবর নেয়ার পালা: সমুদ্র, ঘর, বাচ্চাকাচ্চা, ভবিষ্যৎ, কোনটা ছেড়ে যে কোনটার কথা বলবে সে আরেক মধুর সমস্যা! ওদিকে যে রাতের খাবারের সময় বয়ে যাচ্ছে সেদিকে কারও কোন হুশ নেই! হঠাৎ করেই স্বামী যেন সবকিছু ভুলে আলতো করে স্ত্রীর হাতটা ধরে। তার চুম্বনে সেই প্রথম স্পর্শের মত লজ্জায় লাল হয়ে যায় স্ত্রী! কাঁচের গেলাসে মদের ফোয়ারা ছোটে।
কিছুক্ষণ পর সাইরেন শোনা যায়। জাহাজে সমবেত হবার সংকেত এটা। কিন্তু স্বামী সে সংকেত কানেই তোলে না। দুপুর একটা বাজার আগ পর্যন্ত স্ত্রীকে ছেড়ে কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই তার।
কিন্তু এ কী হচ্ছে? সে চলে যাচ্ছে নাকি?
হ্যাঁ, তাকে তো যেতেই হবে। জাহাজের সবার সাথে ভোরবেলার প্রার্থনায় একত্রিত হতে হবে যে।
ও আচ্ছা, এই কথা! তা ভোরের প্রার্থনা কখন শুরু হবে?
ঘড়ির কাটার ঠিক পাঁচটায়।
ওহহো! এত ভোরে? কিন্তু এই সারাটা রাত স্ত্রী একা-একা কোথায় থাকবে?
স্ত্রী কোথায় থাকবে সেটা স্ত্রীর ব্যাপার!
মনে মনে কিছু একটা ভেবে স্বামী বেশ মজা পেল। তারপর চট করেই স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলো, হোটেলের কোন্ রুমটা ভাড়া নেয়া হয়েছে। স্ত্রী গিয়ে সেই রুমের দরজার সামনে দাঁড়ালো। ভেতরে যেতে ভীষণ লজ্জা লাগছে তার! স্বামী সন্তর্পণে কাছে এসে গা ঘেষে দাঁড়ালো–চুম্বনে চুম্বনে স্ত্রীর মুখ ভরিয়ে তুললো। তারপর হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলে নিয়ে পায়ের ধাক্কায় দরজা খুলে ফেললো।
–ওয়াও! এত্ত বড় খাট! দেখেতো আস্ত একটা জাহাজ মনে হচ্ছে! এত বড় খাটের কী দরকার ছিল!
স্বামীর কথায় স্ত্রী লজ্জা-রাঙা হয়। অবশ্য চিঠি পড়েই তার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যাচ্ছিল। তারা যে একসঙ্গে হোটেলে থাকবে সে সম্পর্কে সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত চিঠিতে ছিল। এখন তার বাস্তবায়ন হচ্ছে। অতএব, স্বামী আপাতত ভোরের প্রার্থনার জন্য জাহাজে ফেরার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল।
–ধুর! এইসব প্রার্থনা ফার্থনায় কে যায়!
“ছি-ছি! ওভাবে বলতে হয় না। স্বামীর ঠোঁট চেপে ধরলো স্ত্রী। তারপর ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল, “বিছানায় না-থেকে চল আমরা বসে বসে কফি খাই। বিছানাপত্র কেমন স্যাঁতসেঁতে মনে হচ্ছে।”
ঊহ! কী দুষ্টু হয়েছে বউটা, কোত্থেকে যে শেখে এসব দুষ্টুমি! ঠোঁটের ওপর রাখা স্ত্রীর হাতটা ধরে বুকের কাছে নিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি দেয় স্বামী “আচ্ছা! বুঝলাম, সবই বুঝলাম!”
না, মোটেই সব বোঝেনি, সে আসলে আস্ত একটা বোকা।
তাই নাকি? আসলেই বোকা? কিছুই বোঝে না? ঠিক আছে, দেখা যাক কতটুকু বোঝে!
আস্তে করে স্ত্রীর কোমরে হাত দিল স্বামী।
উঁহু, এসব কিন্তু মোটেই ঠিক হচ্ছে না; আচরণে আরও সংযত হওয়া উচিত।
–আচরণে সংযত! এত সোজা? …
ঘড়ির কাটায় যখন রাত দুটো বাজল, তখন পূব-আকাশে রক্তরাঙা সূর্য দেখা দিচ্ছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে রাতের বেলা সূর্য ওঠে]। স্বামী স্ত্রী খোলা জানালায় বসে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল। ওরা এখনো যেন প্রেমিক-প্রেমিকাই রয়ে গেছে, তাই না? হুম… কিন্তু অনেক হয়েছে, ক্যাপ্টেন সাহেবকে এবার উঠতে হবে। আবার দশটায় ফেরত আসবে সে। তখন একসঙ্গে নাস্তা করে দুজনে নৌকায় ঘুরতে বের হবে।
যাবার আগে স্বামী নিজ হাতে কফি বানাল। ওরা যখন পাশাপাশি বসে কফি খাচ্ছিল, তখন সবেমাত্র সূর্য উঠতে শুরু করেছে, গাংচিলের ডানায় নতুন দিনের আহবান। দূরের সমুদ্রে গানবোটগুলোকে দেখা যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন সাহেব বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। ঘড়ির কাটাগুলো এখন সূর্যের আলোয় চকচক করছে। নাহ্, আর একটুও দেরি করা যাবে না। কিন্তু যেতে যে মন চায় না! যাহোক, খানিক বাদেই আবার মিলনের সম্ভাবনায় এই আপাত-বিরহকে মেনে নিল ওরা। শেষবারের মত স্ত্রীকে চুম্বন করল স্বামী, তলোয়ার খাপে ভরল, তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে। গেল। ব্রিজের কাছে গিয়ে জাহাজে ওঠার ছোট নৌকাটাকে শিস দিয়ে ডাকল। স্ত্রী কিন্তু জানালায়ই দাঁড়িয়ে ছিল। পর্দা দিয়ে নিজেকে এমনভাবে আড়াল করে রেখেছিল, যেন দেখা দিতে ভীষণ লজ্জা লাগছে! ওদিকে নৌকা না-আসা পর্যন্ত স্ত্রীকে চুম্বন ছুঁড়ে দিচ্ছিল স্বামী। নৌকায় ওঠার সময় চিৎকার করে বলল–“ভালো করে ঘুমিয়ে, স্বপ্নে দেখা হবে।” নৌকা ছেড়ে দিল। স্বামী এবার দূরবীন দিয়ে স্ত্রীকে দেখার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত, কালো-চুলে-জড়ানো একটা ছোট্ট শরীর দেখা যাচ্ছিল। সূর্যরশ্মি এসে পড়ছিল সেই মায়াবী শরীরটার ওপর। মনে হচ্ছিল যেন কোন কল্পনার মৎস্যকুমারী এসে জানালার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।
যথাসময়ে তোপধ্বনি হল। রণভেরীর দীর্ঘ আওয়াজ চকচকে জলের ওপর দিয়ে গিয়ে ছোট ছোট দ্বীপ ছাড়িয়ে দূরের পাইন বন থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। জাহাজের সব নাবিক এসে ডেকের ওপর একত্রিত হয়েছে। কিছুক্ষণ পর ভোরের প্রার্থনা শুরু হলো। এমন সুন্দর সকালের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইবেল থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনানো হলো।
দালাড়ো শহরের ছোট্ট গীর্জায় ঘণ্টা বাজতে শোনা গেল। রবিবারের ঘণ্টা। আজ সবকিছুই যেন কেমন ফুরফুরে। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চেপে সাগরের বুকে অগণিত ছোট ঘোট নৌকা ভেসে বেড়াচ্ছে, নানান রঙের নিশান সেগুলোতে। ব্রিজের ওপর মনের আনন্দে কপোত-কপোতী ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেলে নৌকার হাকডাকে চারপাশ মুখরিত; আর এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে, সূর্য যেন তরঙ্গ-সংকুল জলে নিজের সবটুকু জ্যোতি ঢেলে দিচ্ছে। এমন স্বর্গীয় পরিবেশে কী যেন কী মনে পড়ে যাওয়ায় স্ত্রীকে হঠাৎ লজ্জারাঙা হাসি হাসতে দেখা গেল।
দশটার সময় বারো জন নাবিক জাহাজ থেকে নামলেন। এদের মাঝে আমাদের ক্যাপ্টেন সাহেবও আছেন। অতএব, স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটলো। হোটেলের বিশাল ডাইনিং রুমে ওরা একসাথে নাস্তা করতে বসল। ওদের হাবভাব দেখে আশপাশের টেবিলে নানান রকম কানাঘুষা চলতে লাগলো–“এরা কি সত্যিই স্বামী-স্ত্রী?” ওরা কিন্তু এতে বেশ মজাই পেল; স্বামীর প্রেমিকসুলভ আচরণ যেন আরও বেড়ে গেল। স্ত্রী অবশ্য একটু একটু লজ্জা পাচ্ছিল–একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসে, আবার ডিনার ন্যাপকিন দিয়ে একটুখানি খোঁচা দেয়।
নাস্তা শেষে ওরা ঘুরতে বেরুলো। ব্রিজের কাছে নৌকা বাঁধা ছিল। দুজনে হাত ধরাধরি করে উঠল। স্ত্রী বসল নৌকার হালে, স্বামীর হাতে বৈঠা। তবে মন কিন্তু বৈঠায় নেই। বারবার সে শুধু স্ত্রীর দিকেই তাকায়। স্ত্রীর ছোট্ট নরম গাল, মায়াভরা গভীর চোখ, ঝলমলে পোশাক, সবকিছু মিলিয়ে এক দুর্নিবার আকর্ষণে চোখ যে ফেরানোই যায় না। স্ত্রী কিছুক্ষণ
পর বাতাসের দিকে মুখ করে বসল। উত্তঙ্গ বাতাসের ঝাঁপটা এসে বারবার। তার পোশাক এলোমেলো করে দিচ্ছিল। কোনমতে আবার টেনেটুনে সেগুলো ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলো। স্বামী চুপচাপ বসে সবকিছু দেখছিল আর মিটমিট করে হাসছিল। ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিলো স্ত্রীর সাথে কথা বলতে। শেষমেষ একটা বুদ্ধি করল–ইচ্ছে করেই আনাড়ির মত নৌকা চালাতে শুরু করলো। নৌকা একবার এদিক যায়, তো পরমুহূর্তে ওদিক যায়। স্ত্রী রাগ। করে বকাঝকা করতে শুরু করল। স্বামী কিন্তু তাতে বেশ মজাই পেল। উৎসাহভরে বকা খেল, আর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর তার মাথায় এক নতুন দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলা করল–স্ত্রীকে প্রশ্ন করল, “আচ্ছা। আমাদের বাবুটাকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন?”
স্ত্রীকে দেখে বোঝা গেল না দুষ্টুমিটা সে বুঝেছে কি না। বেশ সরলভাবে পাল্টা প্রশ্ন করল, “বাবুকে আনলে ঘুমাতে দিতাম কোথায়?”
“কেন? আমাদের বিশাল জাহাজে!” স্বামীর ঠোঁটের কোণায় দুষ্টু হাসি।
স্ত্রী বোধহয় এবারে কিছুটা আঁচ করতে পারলো–কিছু না-বলে হাসতে লাগল। সে হাসি স্বামীর হৃদয়ে প্রশান্তির আলোড়ন তুললো। তার দুষ্টুমি কিন্তু তখনও শেষ হয়নি, প্রসঙ্গ বদলাবার ভান করে জিজ্ঞেস করল,
“হোটেলের মালকিন তো আমাদের পাশের রুমেই থাকেন, না?”
–হুঁ।
–সকালে কিছু বলেছেন?
–কেন? কিছু বলার কথা ছিল?
–না, মানে, গতরাতে তার ঘুম হয়েছে কি না?
–কেন? সকালবেলা উঠেই আমাকে হঠাৎ এ কথা বলবেন কেন?
“তা-তো আমি বলতে পারবো না! হতে পারে ঘরে ইঁদুর ঢুকল, কি জানালায় খসখস শব্দ হল; কিংবা আরও কত ধরনের শব্দেই তো একজন বয়স্ক মহিলার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তাই না?”
“উফ! তুমি যদি এসব বন্ধ না-কর তাহলে কিন্তু এবার ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেব!” রাগের অভিনয় করল স্ত্রী। দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। কিছুক্ষণ পর একটা ছোট্ট দ্বীপের কাছে নৌকা ভেড়াল ওরা। খাবারদাবার নামিয়ে লাঞ্চ সেরে নিল। খানিক জিরিয়ে নিয়ে রিভলবার দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করল কিছুক্ষণ। আনন্দে বৈচিত্র্য আনতে কিছুক্ষণের জন্য একটা রডকে বল্লমের মত বানিয়ে মাছ শিকার করার চেষ্টা করল। তেমন সুবিধা করতে না পারলেও এটাকে ওদের কাছে বেশ মজার একটা খেলা মনে হল। বেশ কিছুক্ষণ এই খেলা খেলার পর নৌকায় ফিরল। এবার যাত্রা অসীমের দিকে, নির্মল সৌন্দর্যের দিকে যেখানে তুলতুলে রাজহাঁসেরা জলকেলি করে, আর মাছেরা সাঁতার কেটে বেড়ায় পরম আনন্দে। তবে, এই নির্মল সৌন্দর্যের মাঝেও স্বামী কিন্তু স্ত্রীর সৌন্দর্যকে ভুলল না; বারে বারে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে, চুম্বন করে কখনোই যেন সে ক্লান্ত হয় না…
ঠিক এভাবেই ছয়টি গ্রীষ্ম পার হল। প্রতিবারেই ওদের তারুণ্যের উজ্জ্বলতা সমানভাবে প্রকাশ পেত। আগের বারের মতই প্রাণোচ্ছল, আগের বারের মতই পাগল-পাগল ভাব, আর অবশ্যই আগের বারের মতই সুখী। শীতকালটা ওরা স্টকহোমে নিজেদের ছোট্ট বাড়িটায় কাটাত। এ-সময়টা ওদের জন্য বেশ মজার হত। স্বামী বাচ্চাদের জন্য নৌকা বানিয়ে দিত, কখনো চীন কিংবা দক্ষিণের সমুদ্রের দ্বীপগুলোতে তার দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প বলত, আর বাচ্চারা বড়বড় চোখ করে সেসব শুনতো। মাঝে মাঝে স্ত্রীও নানা কাজের ছুতোয় বাচ্চাদের আশেপাশে ঘুরঘুর করত, মজার কোন গল্প শুনলে হেসে লুটোপুটি খেত। পুরো ঘরজুড়ে কেমন একটা শান্তির আবেশ তৈরি হত। জগতের কোথাও যেন আর এমন দ্বিতীয়টি হয় না। বাচ্চাদের বাবার গল্পে ক্ষণে-ক্ষণে নতুনতর ঘটনার অবতরণা হত। কখনো জাপানের সূর্য, কখনো ভারতের মন্দির, অষ্ট্রেলিয়ার নৌকা-বর্শা আবার কখনোবা নিগ্রোদের উদ্দাম নৃত্য আর শুঁটকি মাছের গল্প হত। দুনিয়ার কোথায় ভালো আখ হয়, কোথাকার আফিম বিশ্বখ্যাত ইত্যাদি হাজারো গল্পের ছড়াছড়িতে বাচ্চারা মুগ্ধ হয়ে থাকত। তারা হয়ত লক্ষ্যই করত না যে, দিন-দিন বাবার মাথার চুল পাতলা হয়ে আসছে। বাবার নিজেরও অবশ্য এ-নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না; কারণ, বাড়ির বাইরে সে খুব একটা যেত না। যদিওবা যেত, সেই পুরোটা সময় বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যেই তার মন পড়ে থাকত–সেখানেই যে তার স্বর্গ লুকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব এলে তাদের সঙ্গে তাস খেলত, কদাচিৎ বারে গিয়ে একটু-আধটু মদপান করত। শুরুর দিকে যখন বাড়িতে তাস খেলা হত, তখন স্ত্রীও মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে খেলতে বসে যেত। কিন্তু এখন তার চার-চারটি সন্তান হয়েছে, সাংসারিক ব্যস্ততাও বেড়েছে। ফলে, আগের মত অতটা সময় নিয়ে আর বসা হয় না এখন। তবুও মাঝেমধ্যে একটু আধটু সময় বের করে খেলা দেখতে বসে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কোন না-কোন কাজে উঠে যেতে হয়। আর যখনই স্বামীর চেয়ারের পাশ দিয়ে যায়, স্বামী আস্তে করে কোমর জড়িয়ে ধরে কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, “হাতের আসল কাজ আসলে এটাই!”
*** *** ***
এবারের যাত্রায় জাহাজ নিয়ে অনেক দূরে যেতে হবে। পুরো যাত্রা শেষ করে বাড়ি ফিরতে প্রায় ছ’মাস লেগে যাবে। ক্যাপ্টেন সাহেবের মনটা ভীষণ খারাপ–বাচ্চারা বড় হচ্ছে, দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছে। এত দায়িত্ব স্ত্রীর একার ওপর রেখে যেতে মোটেই মন মানছিল না। তাছাড়া, নিজেরও বয়স বাড়ছে; আগের সেই উদ্দামতার অনেকটাই এখন ভাটার দিকে। কিন্তু তবুও কিছু করার নেই, চাকরি বলে কথা! যেতে তাকে হবেই। অগত্যা সমুদ্রের উদ্দেশে বাড়ি ছাড়লেন ক্যাপ্টেন সাহেব। শুরুতে পৌঁছলেন ক্রনবার্গ। সেখান থেকে স্ত্রীকে লিখলেন০০
প্রাণপ্রিয় বধূয়া,
চারদিকে শান্ত বাতাস বইছে। শুধু আমার ভেতরটা ভীষণ অশান্ত। ভাবতেও পারছি না, তোমাদের ছেড়ে এত দূরে রয়েছি। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় আমার যে কী পরিমাণ কষ্ট হচ্ছিল সেটা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। যখন জাহাজ ছাড়ল (সন্ধ্যে ছ’টা, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শনশন বাতাস বইছিল) তখন মনে হল যেন আমার বুকের মধ্যে কেউ প্রচণ্ড জোরে পেরেক ঠুকছে, কানের মধ্যে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন সবরকম বোধশূন্য হয়ে গেছি। জাহাজের অন্যরা বলাবলি করছিল–নাবিকরা নাকি অশুভ কিছুর সংকেত আগে থেকেই পেয়ে যায়। জানি না এর সত্যতা কতখানি, তবে তোমার কোন চিঠি না-পাওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি পাচ্ছি না।
আমার এদিককার কোন খবর নেই; কারণ কোন কিছুকেই আমার কাছে খবর বলে মনে হয় না। তোমাদের খবর কী? বাড়ির সব ভালোতো? ববের জন্য একজোড়া জুতো পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছো? ওর পছন্দ হয়েছে তো? এই ছোট-ছোট মুহূর্তগুলো কাছে থেকে দেখতে পারলে খুব ভালো হত। কিন্তু কী করা যাবে বলো? আমার মত হতভাগা তো আর হয় না। যাহোক ভালো থেকো। আজ এ পর্যন্তই।
‘X’ এই ক্রশ চিহ্নে চুম্বন করলে আমার স্পর্শ পাবে।
ইতি
তোমার জনম-জনমের সাথী।
পুনশ্চঃ তুমি বরং সময় কাটানোর জন্য কোন বন্ধু খুঁজে নাও (অবশ্যই মেয়ে বন্ধু)। আর দালাড়ো হোটেলের মালকিনকে বলল, আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত যেন আমাদের রুমের সেই ‘জাহাজটাকে যত্ন করে রাখে।
পোর্টমাউথ পৌঁছে ক্যাপ্টেন সাহেব চিঠির উত্তর পেলেন–
জনম-জনমের সাথী,
বিশ্বাস কর, তোমাকে ছাড়া আমার একটা মুহূর্তও কাটতে চায় না। কিন্তু কী করবো বলো? এদিকে এতকিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় যে সময় কোন দিক দিয়ে চলে যায় বুঝতেও পারি না। নতুন দুঃশ্চিন্তা শুরু হয়েছে এলিসকে নিয়ে দাঁত উঠেছে তোমার মেয়ের। কিন্তু ডাক্তার বলেছেন, সাধারণত এত শীঘ্র দাঁত ওঠার কথা না, এটা আসলে…লক্ষণ (তোমাকে বলতে চাচ্ছি না)। ববের পায়ে জুতো ঠিকমত লেগেছে, পছন্দও হয়েছে। নতুন জুতো পরে সে মসমঁসিয়ে হেঁটে বেড়ায়।
তুমি বলেছিলে কোন বান্ধবী খুঁজে নিতে। জানলে খুশি হবে, আমি খুব ভালো একজন বান্ধবী পেয়েছি। অবশ্য এটা বলা ভালো যে, সে-ই বরং আমাকে খুঁজে নিয়েছে। ওর নাম ওটিলিয়া স্যান্ডারগ্রীন। ক্যাথলিক কলেজে লেখাপড়া করেছে। ওর চিন্তা-ভাবনা অনেক গভীর, জীবনবোধও বেশ স্পষ্ট। অতএব, তোমার বউ গোল্লায় যাবে ভেবে দুঃশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। ও যথেষ্ট ধর্মমনা। ওর সাথে কথা বলে মনে হয়েছে, ধর্মকে আমাদের আরও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা উচিত। যাহোক, সব মিলিয়ে ও চমৎকার একটা মেয়ে। তোমাকে লিখতে-লিখতেই এইতো ওটিলিয়া এসে গেল। ও তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।
ইতি
তোমার গুরলী
চিঠিটা হাতে পেয়ে যতটা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, পড়ার পর তার অনেকটাই নিভে গেল ক্যাপ্টেন সাহেবের। কোথায় যেন কী একটা খটকা লাগছে। প্রথমত, চিঠিটা অনেক ছোেট। দ্বিতীয়ত, বউয়ের অন্যান্য চিঠিতে যতটা আবেগ মাখা থাকে তার অর্ধেকও এ চিঠিতে নেই। আর এই ওটিলিয়াটাই বা কে? ওর নাম দু’বার লিখেছে। ক্যাথলিক কলেজ’, ‘ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা কী সব গম্ভীর-গম্ভীর কথাবার্তা। তাছাড়া, আগের মত ‘গুল্লা’ না লিখে লিখেছে ‘গুরলী’। কী হচ্ছে এসব? নাহ্, কিছুতেই যেন মিলছে না। কোথায় যেন কী তাল কেটে যাচ্ছে…
পরের চিঠিটা ক্যাপ্টেনকে আরও ভাবিয়ে তুললো। আগেরটার সপ্তাহখানেক পরে এ চিঠিটা এল বোর্দুয়া থেকে। চিঠির সঙ্গে আলাদা খামে ভরা একটা বইও এসেছে দেখা গেল। যাহোক, নতুন চিঠি হাতে পেয়ে ক্যাপ্টেন আনন্দে আত্মহারা হলেন। তড়িঘড়ি করে খামটা খুলে পড়তে শুরু করে দিলেন।
প্রিয় উইলিয়াম (অ্যাঁ! সম্বোধনে পরিবর্তন!)।
জীবনটা আসলে একটা সংগ্রাম (সে আবার কী! সংগ্রামটংগ্রামের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক!)। কেডরনের নিয়ত বয়ে চলা নদীর মত জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি পুরোটাই এক সংগ্রাম (সে কী রে! কেডরন নদী! তার মানে, বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছে!)। এ নদীর স্রোতের মতই আমাদের জীবনটাও যেন বয়ে চলেছে। মানুষ ঘুমের মধ্যে হাঁটলে যেমন বুঝতে পারে না কতটা বিপদ-সংকুল পথ সে পাড়ি দিচ্ছে, আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমন (ওহহহ! ক্যাথলিক কলেজের শিক্ষা! এগুলো সব ওই ক্যাথলিক কলেজের শিক্ষার প্রভাব)। এরপর হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা নৈতিকতার সম্মুখীন হয়ে পড়ি (এর মধ্যে আবার নৈতিকতা কোত্থেকে এল!)। আমি অনুভব করতে পারছি, আমার ঘুমও ভেঙ্গেছে; আর তাই এখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছি, আমাদের বিয়েকে কি সত্যিকার অর্থেই বিয়ে বলা যায়? কষ্ট হলেও স্বীকার করতে হচ্ছে, উত্তরটা না। কারণ, “ভালোবাসা স্বর্গ থেকে আসে।”( সেন্ট ম্যাথিউ, অনুচ্ছেদ ১১, পৃষ্ঠা ২২,২৪)।
ক্যাপ্টেন সাহেব আর স্থির থাকতে পারছিলেন না। তাঁর দুনিয়াসুদ্ধ কাঁপছিল। কিন্তু চিঠির পুরোটা তখনও শেষ হয়নি। নিজেকে স্থির রাখতে এক গ্লাস রামের সাথে পানি মিশিয়ে এক ঢোকে পেটে চালান করে দিলেন। এবার চিঠির বাকি অংশ পড়তে শুরু করলেন
“আমাদের ভালোবাসার পুরোটাই আসলে পার্থিব। আমরা কখনোই আত্মা দিয়ে একে-অন্যকে চিনিনি। প্লেটো যে ভালোবাসার কথা বলেছেন, তার ধারেকাছেও যেতে পারিনি আমরা। কখনো ভেবে দেখেছো, আমাদের ভালোবাসায় আত্মার মিলন হয়েছে কি না? আমাদের আত্মা একে-অপরকে কখনো চিনেছে কি না? (ফাইডন, গ্রন্থ ৬, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ৯)। আমি জানি, এখানেও উত্তরটা ‘না’-ই হবে। তাহলে তোমার কাছে আমার অবস্থানটা কী? শুধুই একজন গৃহকর্মী? তোমার রক্ষিতা? উহ! কী লজ্জার কথা, কী অসম্মানের কথা। ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে আমার।”
ওহ্! আর সহ্য হচ্ছে না। ওই ডাইনি ওটিলিয়া চুলোয় যাক, চুলোয় যাক ওর ক্যাথলিক কলেজের সব বিদ্যা। গুরলী আমার গৃহকর্মী! ওহ্! আমি স্বপ্নেও কখনো এমন ভাবতে পারি না। ও আমার স্ত্রী, আমার সন্তানদের মা। অথচ, ও কীভাবে এমন কথা লিখতে পারলো?
যাহোক, চিঠির শেষ অংশটুকু এমন–
“চিঠির সঙ্গে একটা বই পাঠিয়েছি। বইটা ভালো করে পড়লে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পাবে। শত শতাব্দী জুড়ে স্ত্রী-জাতির হৃদয়ে চেপে রাখা অব্যক্ত বেদনার কথাই বলা হয়েছে বইটাতে। বলা হয়েছে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের করা অন্যায় আর অবজ্ঞার কথা। পুরো বইটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে, চিন্তা করে দেখো আমাদের মিলনকে সত্যিকারের ‘বিয়ে’ বলা যায় কি না। তারপর চিঠির উত্তর দিও।
ইতি
গুরলী
চিঠিটা হাতে নিয়ে ক্যাপ্টেন সাহেব কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। অলুক্ষণে কিছুর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু কিছুতেই মাথায় আসছে না স্ত্রীর কী এমন হল যে তার চিন্তা-ভাবনায় এতটা পরিবর্তন এলো। তবে যা-ই হোক না কেন, সেটাকে অবশ্যই ধর্মচিন্তা বলা যাবে না, কারণ, আদতে এইসব চিন্তা-ভাবনা ধর্ম নিয়ে প্রতারণার সামিল। চট করে উঠে চিঠির সাথে পাঠানো বইটার ওপরের খাম ছিঁড়ে ফেললেন তিনি–এ ডলস হাউস’, হেনরিক ইবসেন। আচ্ছা, এই তাহলে! বইয়ের নামটা তো ভালোই মনে হচ্ছে। তাদের বাড়ি একটা চমৎকার পুতুলঘর, স্ত্রী তার ছোট পুতুল আর তিনি স্ত্রীর বড় পুতুল। জীবনের কঠিন পথ তারা একসঙ্গে নেচে-গেয়ে পাড়ি দিয়েছেন–সুখী হয়েছেন। জীবনের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কি ই-বা চাইবার থাকতে পারে? বইটার নাম অনুযায়ী তো মনে হচ্ছে, এসব কথাই ওতে লেখা থাকার কথা। কিন্তু স্ত্রীর চিঠি পড়েতো তা মনে হল না। নিশ্চয়ই কিছু গড়বড় আছে। বইটা এখনই পড়ে বুঝতে হবে সমস্যাটা কোথায়।
পরবর্তী তিন ঘণ্টার মধ্যে ক্যাপ্টেন সাহেব বইটা পড়ে শেষ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু মেলাতে পারলেন না। এ বইয়ের সঙ্গে তাঁর নিজের কিংবা তাঁর স্ত্রীর মিল কোথায়? তারা কি কোন দলিল জালিয়াতি করেছে?–না। তারা কি একে-অন্যকে ভালোবাসেনি? অবশ্যই বেসেছে। তাহলে এই বই পড়ে বিচলিত হবার কী আছে? স্ত্রী তাকে এই বইটা পাঠালোই-বা কেন? উঁহু! নিশ্চয়ই খুব সূক্ষ্ম কিছু বাদ পড়েছে। ক্যাপ্টেন সাহেব এবার বইটা নিয়ে নিজের কামরায় গেলেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন। এবার আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো লাল-নীল কালি দিয়ে দাগিয়ে পড়তে থাকলেন। কখন যে রাত ফুরিয়ে ভোর হল খেয়ালই হল না। মনোযোগ দিয়ে দ্বিতীয়বারের মত পুরো বইটা পড়ার পর স্ত্রীকে লিখলেন–
‘এ ডলস হাউস’ নাটকের পর্যালোচনা
১. ভদ্রমহিলা ঐ লোকটিকে বিয়ে করেছিল, কারণ সে জানত, লোকটি তাকে ভালোবাসে। এখানে সে বেশ সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। সে যদি কারও প্রেমে পড়ার অপেক্ষায় থাকত, তাহলে হয়ত এমনও হতে পারত যে, ভদ্রলোকটি তার প্রেমে পড়তই না। কারণ, দু’পক্ষ একই সময়ে, সমানভাবে, একে-অন্যের প্রেমে পড়েছে এমন ঘটনা বিরল।
২. ভদ্রমহিলা দলিল জাল করেছিল। স্বীকার করতেই হবে, এখানে সে বড় একটা বোকামি করেছে। কিন্তু কাজটা সে শুধুমাত্র তার স্বামীর জন্য করেছে সেটা সত্য নয়। কারণ, স্বামীকে সে কখনোই সত্যিকারে ভালোবাসেনি। সে যা করেছে, তা দায়িত্ব মনে করে করেছে। তাই, সে যদি বলত, কাজটা সে তার স্বামী-সন্তান এবং নিজের জন্য করেছে তাহলে বরং সেটা গ্রহণযোগ্য হত।
৩. নোরার নাচ শেষে হেলমারের তাকে আলিঙ্গন করতে চাওয়াটা যে শুধুই তার ভালোবাসার নিদর্শন সেটাতো ঠিক। কিন্তু হেলমার হয়ত আরও অনেক কিছুই করতে চায় যা মঞ্চে দেখানো সম্ভব নয় বলে নাট্যকার তা বাদ দিয়েছেন। ফরাসী একটা প্রবাদ আছে জানো তো “অনেক কিছুই করা যায়, যার সবকিছু দেখানো যায় না। কিন্তু নাট্যকার যদি সত্যিই নিরপেক্ষ হতেন তাহলে তিনি অন্য পক্ষের চাওয়ার কথাও অবশ্যই উল্লেখ করতেন। ওলেন্ডার বলেছেন “মাদী সারমেয় চায়, আর মর্দা সারমেয় আদায় করে নেয়।” (দালাডোর সেই ‘জাহাজ’র কথা মনে করে দেখো।)।
৪. নোরা যখন আবিষ্কার করল, তার স্বামী আসলে মূর্খ (তখনই আবিষ্কৃত হল যখন তার কৃত অপরাধ প্রকাশিত না-হওয়ায় স্বামী তাকে ক্ষমা করতে চাইছে) তখন সে তার সন্তানদের ফেলে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, সন্তান প্রতিপালনের জন্য নিজেকে অযোগ্য মনে করল। নষ্টামির এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এটা। নিজেকে সে খুব চালাক মনে করত। কিন্তু তা না-করে নিজেকে যদি বোকা বলে ভাবতে পারত, তাহলে বরং তারা দুই বোকা (পুরো নাটকেই স্বামীকে সে বোকা বানিয়ে রেখেছে) মিলেমিশে সুন্দর করে সংসার করতে পারত (একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না, ক্যাথলিক কলেজে দলিল জাল করাকে নিশ্চয়ই পূণ্য হিসেবে শেখানো হয় না?)। যাহোক, সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হচ্ছে, সে তার সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্ব সেই লোকটার কাছেই দিয়ে গেল যাকে সে নিজে ভীষণ ঘৃণা করে। এটা কি স্পষ্ট স্বার্থপরতা নয়?
৫. নোরা যদি সত্যিই তার স্বামীকে নির্বোধ মনে করে থাকে, তাহলে, তার উচিত ছিল অমন নির্বোধ লোকের কাছে সন্তানদের ছেড়ে না দিয়ে বরং নিজের সেখানে থেকে যাওয়া।
৬. নোরার কূটবুদ্ধি দিয়ে হাসিল করা কাজগুলোকে প্রশংসা করেনি বলে স্বামীকে দোষ দেয়া ঠিক হবে না। কারণ, নাটকের শেষ মুহূর্তের আগে সে জানতই না যে, তার স্ত্রী এমন কূটচাল চালতে পারে। নোরা নিজের আসল চরিত্র সব সময়ই স্বামীর কাছে গোপন করেছে।
৭. পুরো নাটকে নোরা আসলে বোকামিই করেছে। সে নিজেও পরবর্তীতে তা বুঝতে পেরেছে কিন্তু মেনে নিতে পারেনি।
৮. সব দিক পর্যালোচনা করে বলা যায়, ওরা একসঙ্গে থাকলে কিন্তু ভবিষ্যতে বেশ সুখে থাকতো। কারণ, নোরার স্বামী তার ভুল বুঝতে পেরেছিল, নোরা নিজেও বুঝতে পেরেছিল যে তার সব আচরণ ঠিক ছিল না।
যাহোক, নাটক নিয়ে আর না। সবকিছু ভুলে চল আমরা আবার নতুন করে শুরু করি। এই আমি আমার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমাদের তো কিছুই হারায়নি। স্বীকার করে নিচ্ছি, আমরা দুজনেই বোকা। তুমি হচ্ছো ছোট্ট নোরা, যাকে ভালোভাবে আদর-যত্ন করা হয়নি; আর আমি হচ্ছি বুড়ো হাদারাম, যে এতদিন ভালোভাবে জানতই না কীভাবে আদর-যত্ন করতে হয়। আসলে আমরা দুজনেই করুণার পাত্র। কিন্তু কী আর করা যাবে, বল? বড়জোর তাদেরকে মন জুড়িয়ে গালাগাল করা যায় যারা আমাদের এসব শেখায়নি। পুরুষ মানুষ হলেও আদপে আমি কিন্তু তোমার মতই কোমল। হয়ত খানিকটা বেশিও হতে পারি! কারণ, আমি বিয়েই করেছি শুধুমাত্র ভালোবাসার জন্য, তোমাকে নিয়ে ঘর করবো বলে। অতএব, সবকিছু ভুলে চল আমরা বন্ধু হয়ে যাই, আর জীবনের পাঠশালায় যা কিছু নিজেরা শিখেছি তা আমাদের সন্তানদেরও শেখানোর চেষ্টা করি।
আর শোন, তোমার পাঠানো বইটা আগাগোড়া পড়ে মন্তব্য তো পাঠালাম; কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ, এর বিষয়বস্তু আমাদের জীবনের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ কি না? আমরা কি একে-অন্যকে ভালোবাসিনি? একে-অন্যের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিনি? মনে করে দেখ, শুরুর দিকে অনেক বিষয় নিয়েই আমাদের মনোমালিন্য হত; কিন্তু পরবর্তীতে আমরা কি সেগুলোকে শুধরে নিইনি? এ তোমার কেমন খামখেয়ালী শুরু হল, বলো তো? আমার এসব একদম ভালো লাগছে না। ওই ওটিলিয়া আর ওর ক্যাথলিক কলেজের গুষ্টিসুদ্ধ নরকে যাক। যে বইটা তুমি পাঠিয়েছ সেটা আসলে একটা হতচ্ছাড়া-বাজে বই। এটাকে এমন একটা জাহাজের সঙ্গে তুলনা করা যায় যার মধ্যে যাত্রীদের বাঁচানোর মত যথেষ্ট সংখ্যক বয়া নেই। ফলে যাত্রীরা ডুবে মরে। আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে একটা বয়া পেয়েছি, কিন্তু একবার এটা হারিয়ে ফেললে দ্বিতীয়বার হয়ত আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। তোমার কি মনে হয় না, যে বাদামের খোসা ফাটালে ভেতরে পঁচা বেরুবে সে বাদাম না ফাটানোই ভালো? আমার তো মনে হয়, সে বাদাম শুধু শয়তানের জন্য তুলে রাখা রাখা উচিত। যাহোক, প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো, তোমার স্বাভাবিক বোধ আবার ফিরে আসুক।
বাচ্চারা কেমন আছে? তুমি কিন্তু ওদের কথা উল্লেখ করতে ভুলেই গেছ। বোধহয় নোরার হতভাগ্য বাচ্চাগুলোকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিলে, তাই না? (অবশ্য অমন হতভাগ্য বাচ্চা শুধু অমন হতভাগা নাটকেই দেখা যায়!)। আমার ছোট্ট সোনা ছেলেটা কি কাঁদছে? আমার ফুটফুটে নাইটিংগেল পাখি কি গান গাইছে? আর সর্বোপরি, আমার প্রাণের পুতুল নেচে বেড়াতে ভুলে যায়নি তো? অবশ্য সে যদি চায়, তার জীবনসঙ্গী সুখে থাকুক তাহলে তার ভুলে যাবার কথা নয়। যাহোক, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, যাবতীয় অমঙ্গল থেকে তোমাকে দূরে রাখুন। আমাদের দুজনের মাঝে যেন কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয় এমন প্রার্থনাই করি। তোমাকে হয়ত শেষ পর্যন্তও বোঝাতে পারলাম না আমার মন কতটা খারাপ হয়েছে। বসে বসে মনজুড়িয়ে বইটাকে গালিগালাজ করতে পারলে হয়ত খানিকটা শান্তি পেতাম। যাহোক, এখন থাক সেসব কথা, ঈশ্বর আমাদের সন্তানদের মঙ্গল করুন। ওদের ছোট্ট গালে আমার আদর দিও।
ইতি
তোমার বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গী
চিঠিটা পোস্ট করার পর ক্যাপ্টেন সাহেব অফিসারদের মেসে গেলেন। সেখানে খানিকটা মদ্যপান করলেন। জাহাজের ডাক্তারও সেসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ক্যাপ্টেন সাহেব ডাক্তারের দিকে ফিরে এলোমেলোভাবে বললেন, “বাতাসে বারুদের গন্ধ পাচ্ছ? আমি কিন্তু পাচ্ছি। এখন আমি টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, যাতে আমার ওপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব-উত্তর দিক থেকে বাতাস বয়ে যায়।”
ডাক্তার সাহেব ক্যাপ্টেনের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। কথায় মাতলামির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে।
–ওহ! ওটিলিয়া! ওটিলিয়া! ওই মাগী চায়টা কী? ও আমার হাতে জব্দ হতে চায়। ডাইনিটাকে লেবারদের মেসে ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে রাখতে পারলে ভালো হত। আমি জানি, ওর মত বুড়ি-মাগীর জন্য এটাই উপযুক্ত হবে।
এবারে ডাক্তার সাহেব খানিকটা এগিয়ে এলেন। উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছে, বন্ধু?”
ক্যাপ্টেন আবার হেড়ে গলায় চিৎকার করলেন–“প্লেটো, এই শালা প্লেটোই যত নষ্টের গোড়া। ছয় মাস সমুদ্রে থাকলে বুঝতো প্রেম কাকে বলে। এই শালা আবার নৈতিকতার কথা বলে! নৈতিকতা,অ্যাঁ? রাইফেলের বাট দিয়ে পিটিয়ে তোর নৈতিকতা বের করে ছাড়বো, শালা! কোথায় ওটিলিয়া? ওই শালী বিয়ে করলে তখন আর মুখে প্লেটোর কথা ফুটতো না।”
ক্যাপ্টেনের পাগলামিতে ডাক্তার সাহেব এবার বিরক্ত হলেন, “ওফ! তোমার হয়েছেটা কী?”
–কিছু না। কিছু হয়নি আমার। ওহহহ! তুমিতো ডাক্তার, না? হ্যাঁ, তুমিই ভালো জানবে। আচ্ছা, বলোত এই ভাতারছাড়া মাগীগুলোর সমস্যাটা কী? তোমার কী মনে হয়, বিয়ে না-করে থাকা কি ভালো কথা? ওদের কি বিয়ে করার ইচ্ছে জাগে না? ওদের কি… লাগে না?
ক্যাপ্টেনের বকবকানি আর দাঁত খিঁচুনি দেখে ডাক্তার সাহেব শেষপর্যন্ত হো হো করে হেসেই দিলেন। তারপর, বক্তৃতা দেয়ার মত করে শুরু করলেন, “দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, জগতে নারী-পুরুষের সংখ্যার অনুপাত সমান নয়। বরং, পুরুষের সংখ্যাই কম। ফলে, সব নারীর পক্ষে বিয়ে করাটা সম্ভব হয় না। তবে প্রকৃতিতে কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতিতে বেশিরভাগ পুরুষ প্রাণীই বহুগামী, আর এক্ষেত্রে তাদের তেমন কোন বাধাও পেতে হয় না। কারণ সুস্থতা এবং সবলতাই প্রকৃতিতে টিকে থাকার প্রধান হাতিয়ার। এ-কারণে, সঙ্গীহীন নারী পশু প্রকৃতিতে দেখা যায় ্না। কিন্তু সভ্য সমাজে এমনটা দেখা যায়। সভ্য দেশগুলোতে, যেখানে নারী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করে, সেখানে একজন পুরুষের যথেষ্ট পরিমাণ জীবিকা অর্জন করাটা কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার; কারণ তাদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি। তাই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও একজন নারীকে যদি সঙ্গীহীন থাকতে হয়, তাহলে মানতেই হবে, তার কপাল খারাপ। এমন নারীদের প্রতি সবার সহানুভূতি দেখানো উচিত।”
–সহানুভূতি! ঠিক আছে, তা না-হয় মানলাম। কিন্তু ওরা নিজেরা কি অন্যের প্রতি সহানুভুতিশীল?”
ক্যাপ্টেন সাহেব এবার ডাক্তারকে সব ঘটনা বললেন। এমনকি, তিনি যে সবেমাত্র এ জাতীয় একটা নাটক পড়েছেন তাও বললেন। সব কথা শুনে ডাক্তার সাহেব মদভর্তি বোতলের ছিপির ওপর হাত রেখে বেশ বিজ্ঞের মত বললেন, “এসব অর্থহীন লেখালেখির কোন শেষ নেই। এগুলোকে এত পাত্তা দেয়ারও কিছু নেই। একমাত্র বিজ্ঞানই পারে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে।”
*** *** ***
ছ’ মাস ফুরিয়ে এলো। ক্যাপ্টেনের বাড়ি ফেরার সময়ও ঘনিয়ে আসছে। এই পুরোটা সময় জুড়েই স্ত্রীর সঙ্গে তার পত্রালাপ হয়েছে। অবশ্য সেগুলো খুব একটা সুখকর ছিল না (স্ত্রী কঠোর ভাষায় তার সমালোচনার জবাব দিয়েছেন)। যাহোক, অবশেষে একদিন ক্যাপ্টেন সাহেব দালাড়ো বন্দরে নামলেন। তার স্ত্রী, বাচ্চারা, দু’জন কাজের লোক আর ওটিলিয়া আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। স্ত্রী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেও তাকে দেখে খুব একটা আন্তরিক বলে মনে হল না। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে স্বামীর চুম্বন পেতে কপাল এগিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন সাহেব কিন্তু চোখের কোণা দিয়ে ওটিলিয়াকে দেখছিলেন। হারামজাদী জাহাজের মাস্তুলের মত ঢ্যাং-ঢ্যাংয়ে লম্বা, তার-ওপর আবার ছেলেদের মত ছোট করে চুল কাটিয়েছে। পেছন থেকে দেখতে ঠিক একটা ময়লা ন্যাকড়ার মত লাগছে!
রাতে সেই দালাড়ো হোটেলে এসে উঠল ওরা। ব্যাগবোঁচকা রেখে, হাত-মুখ ধুয়ে, খাবার টেবিলে বসল। কেউই অবশ্য তেমন কিছু খেল না। এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ; তারপর শুধু চা খেল। অন্য কোন পানীয় ছুঁয়েও দেখল না। সবশেষে শোয়ার আয়োজন হল। সেই বিশাল জাহাজে এবার ছেলেমেয়েরা ঘুমালো, আর ক্যাপ্টেন সাহেব পড়ে রইলেন চিলেকোঠার এককোণায়। উহ! কি বিশাল পরিবর্তন! ক্যাপ্টেন সাহেব হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছেন। না-না, বিবাহিত হয়েও বউ ছাড়া থাকা, এ কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।
পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন সাহেব স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে বেরুতে চাইলেন। ইচ্ছে ছিল স্টীমারে করে বেড়াবেন। কিন্তু বাদ সাধল ওটিলিয়া। তার নাকি স্টীমারভীতি আছে। তাছাড়া আজ রবিবার (আরে! রবিবার তো কী হয়েছে? হারামজাদী তুই তোর রবিবার নিয়েই থাক!)। অগত্যা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হল। স্ত্রীকে নিয়ে হাঁটতে বেরুবেন তিনি। অনেক কথা জমা হয়ে আছে, একে-অন্যকে অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু এর মধ্যে যেন কোনভাবেই ওটিলিয়া না থাকে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ওটিলিয়াকে এড়ানো গেল–শুধু তারা দুজন বের হলেন। অনেকদিন পর হাত ধরে হাঁটলেন তারা। তবে মুখে খুব বেশি কথা বললেন না। অল্পসল্প যা বললেন তা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য নয়, বরং গোপন করার জন্য। কলেরায় মৃতদের কবরস্থান পার হয়ে সুইস উপত্যকার পথ ধরলেন দু’জনে। পাইন বনে বাতাস লেগে খসখস আওয়াজ হচ্ছিল, আর বড় বড় শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে দূরের নীল সমুদ্রের আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল। স্বামী-স্ত্রী হাঁটতে-হাঁটতে একটা বড় পাথরের কাছে গিয়ে বসলেন। সুযোগ বুঝে ক্যাপ্টেন সাহেব চট করে স্ত্রীর কোলের কাছে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত ঝড়টা শুরু হবে! হলোও তাই, স্ত্রী-ই আগে শুরু করলেন, “আমাদের বিয়ে সম্পর্কে কিছু ভেবেছো?”
–না।
ক্ষণিক নীরবতা। কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন সাহেব নীরবতা ভাঙলেন “পুরো ব্যাপারটাকে আগাগোড়া তলিয়ে দেখে আমার মনে হয়েছে, এটা আসলে ভাবার মত কোন বিষয় নয়। ভালোবাসা হৃদয়ানুভূতির ব্যাপার, হৃদয় দিয়েই এটা চালিত হওয়া উচিত। দড়ি-কাছি বেঁধে, কাটা-কম্পাস ম্যাপ দিয়ে হিসেব করে ভালোবাসা পেতে গেলে ব্যর্থতা অনিবার্য।”
–কিন্তু এটাতো সত্য যে, আমাদের সংসার একটা পুতুলের সংসারে পরিণত হয়েছে।
এবার গলায় একটু জোর দিলেন ক্যাপ্টেন সাহেব–“একমত হতে পারছি না। তুমি কখনো কোন দলিল জাল করনি, কোন ডাক্তারের কাছে হাঁটু উঁচু করে দেখাওনি যাতে পরবর্তীতে তাকে কাজে লাগানো যায়, রোমান্টিকতার নামে তুমি কখনো তোমার স্বামীর সাথে ভালোবাসার মিছে অভিনয় করনি, তুমি কখনোই এতটা বেকুব ছিলে না যে, তুমি সন্দেহ করবে যে দোষ তুমি না বুঝে করেছ তার জন্য তোমার স্বামী তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে; সর্বোপরি, তুমি কখনোই আমার কাছে মিথ্যে বলনি। আর আমিও তোমার কাছে সবসময়ই বিশ্বস্ত থেকেছি। হেলমার যেমন তার ব্যাংকে লোক নিয়োগের ব্যাপারে নোরার হস্তক্ষেপকে খারাপভাবে নেয়নি, আমিও তেমনি আমার সব ব্যাপারে তোমাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দিয়েছি। অতএব, আধুনিক বা সনাতন যে পদ্ধতিতেই বিবেচনা কর না কেন, আমাদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, আমাদের বিয়ে পবিত্র বন্ধন।”
–মানছি তোমার কথা, কিন্তু তুমিও নিশ্চয়ই মানবে, আমি তোমার গৃহকর্মী ভিন্ন অন্য কিছু নই।
–ওহহহ! আবার! ক্ষমা কর, মানতে পারছি না। তোমাকে কখনোই। রান্নাঘরে বসে খেতে হয় না, তোমার নিজের বাড়িতে যে কাজগুলো তুমি। কর তা সামান্য কটা টাকার জন্য কর না, টাকা-পয়সা খরচের ব্যাপারে। তোমাকে কখনো হিসাব দিতে হয় না, তুমি কী করলে বা না করলে সে। জন্য তোমাকে বকা খেতে হয় না। আর তাছাড়া, আমাকে যেসব কাজ। করতে হয় সেগুলো একবার ভেবে দেখ–জাহাজের গতিপথ হিসাব করা, দড়ি-কাছি সামাল দেয়া, হেরিং মাছ আর মদের বোতল গুনে রাখা, আটা ময়দার বন্দোবস্ত করা; সর্বোপরি, তোমাদের ছেড়ে দূরে দূরে থাকা; এগুলো কি তোমার কাজের চেয়ে ভালো কিছু? তার চেয়ে তুমি বরং আস্ত একটা সংসার দেখাশোনা করছ, বাচ্চাদের বড় করে তুলছ, এগুলো কি বেশি গর্বের আর বেশি সম্মানজনক নয়?
–না, কোনভাবেই নয়। তোমার কাজের জন্য তোমাকে মাইনে দেয়া হয়, তুমি স্বাধীন, তোমার ওপর তোমার নিজের কর্তৃত্ব আছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, তুমি একজন পুরুষ মানুষ।
ক্যাপ্টেন এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, “ওহহহ! তুমি কি সত্যিই চাও তোমার কাজের জন্য আমি তোমাকে মাইনে দিই? তুমি কি সত্যিই আমার গৃহকর্মী হতে চাও? ঠিক আছে, না হয় মানলাম পুরুষ হয়ে জন্ম নিয়ে ভুল করেছি। আজকাল তো পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়াটা রীতিমত অপরাধ! কিন্তু এতেতো আমার কোন হাত নেই। সব প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুটো জাত থাকবেই; না হলে তো জগৎ থেমে যাবে। এই দুই জাতের মধ্যে যারা ঝগড়া লাগিয়ে দেয়ার উপক্রম করে তারা যেন নরকে যায়।”
শেষ কথাগুলো বলার সময় ক্যাপ্টেন সাহেবের গলায় আক্ষেপ ঝরে পরছিল। কিন্তু তার আরও কিছু প্রশ্নের জবাব দেবার ছিল
–আচ্ছা, তুমি দাবি করলে তুমি আমার গৃহকমী, অর্থাৎ আমি তোমার প্রভু; কিন্তু ভেবে দেখ তো, তোমার সাথে পরামর্শ না করে আমি কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি কি না। সবসময় আমরা মিলেমিশে সিদ্ধান্ত নিই না? বরং বলা যায়, তোমার অনেক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমার কিছু বলারই থাকে না, তুমি যেভাবে চাও সেভাবেই কর। বাচ্চাদের তুমি পুরোপুরি নিজের সিদ্ধান্তে বড় করছ না? সেবার তোমাকে বললাম, বাচ্চাটা ঘুমানোর সময় ওকে দোলা দিও না, ওতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হতে পারে। কিন্তু তোমার মনে হল, দোলা দেয়াটাই উচিত হবে। অর্থাৎ, আমরা পুরোপুরি বিপরীত সিদ্ধান্তে ছিলাম। এক্ষেত্রে আমাদের আপোস করার কোন উপায় ছিল না; কারণ দোলা দেয়া এবং না দেয়ার মধ্যবর্তী কোন অবস্থা নেই। অতএব, শেষ পর্যন্ত তোমার সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হল। আমি কি এসব নিয়ে কখনো কোন অভিযোগ করেছি?–করিনি। বরং এসব নিয়েই মিলেমিশে আমরা বেশ ভালো আছি। অথচ, ওই ওটিলিয়ার কথা শুনে আজ তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছ!
“সবসময় শুধু ‘ওটিলিয়া’, ‘ওটিলিয়া কর কেন? তুমি নিজেই তো বলেছিলে ওকে জুটিয়ে নিতে।” বেশ ঝাঁঝালো গলায় কথাগুলো বলল স্ত্রী।
–মোটেও না। আমি কখনোই ওটিলিয়াকে জোগাড় করে নিতে বলিনি, বলেছিলাম একজন বান্ধবী জোগাড় করে নিতে। কিন্তু আমার কপাল যে এত খারাপ, তা কে জানত! এখনতো দেখা যাচ্ছে ওটিলিয়াই তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।
“তুমি সব সময়ই আমি যা পছন্দ করি তা থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাও।” স্ত্রীর গলায় স্পষ্ট বিরক্তি।
–আচ্ছা! তাহলে কি তোমার সব পছন্দ শুধু ওই ওটিলিয়াকে ঘিরেই? তোমার কথা শুনে কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।
–তোমার যা-ই মনে হোক না কেন, ওটিলিয়ার এ বাড়িতে আসা বন্ধ করা যাবে না। ওকে আমি মেয়েদের ল্যাটিন শেখানোর দায়িত্ব দিয়েছি। তাছাড়া, মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার অন্যান্য ব্যাপারগুলোও ও-ই দেখে।
স্ত্রীর কথা শুনে আঁতকে উঠলেন স্বামী, “হায় ঈশ্বর! আমার মেয়েরা তো ধ্বংস হয়ে যাবে!”
–সে তুমি যা খুশি বলতে পারো; কিন্তু আমি চাই, একজন পুরুষ মানুষ যা কিছু জানে আমার মেয়েরাও তা জানুক, যাতে ওদের বিয়েটা হয় সত্যিকারের বিয়ে।
–কিন্তু সোনা, সব স্বামীতো ল্যাটিন জানে না। তাহলে তোমার মেয়েদের ল্যাটিন শেখানোর দরকার পড়ল কেন? এই আমাকেই দেখ, আমি তো ল্যাটিন বলতে শুধু ‘অ্যাবালেটিভ’ শব্দটাই জানি! তাতে কি আমাদের সংসারে সুখের কমতি পড়েছে কখনো? তাছাড়া, তুমি হয়ত জেনে থাকবে, ছেলেদের ল্যাটিন শেখানো বন্ধ করানোর জন্য সম্প্রতি একটা আন্দোলন হয়েছে। এর উদ্যোক্তাদের মতে, বাচ্চাদের এত গুরুগম্ভীর ভাষা শেখানোর কোন মানে হয় না। এতকিছুর পরও কি তুমি বুঝতে পারছ না? তোমার কি মনে হচ্ছে না, এসব শিখতে গিয়ে ছেলেরা ইতোমধ্যে ধ্বংসের দিকে যথেষ্ট পরিমাণ এগিয়েছে? এখন জোর করে ছেলেদের সমান হতে গিয়ে মেয়েদেরও কি সে পথে এগুতে হবে? ওহ্! ওটিলিয়া! ওকে পেলে। জিজ্ঞেস করতাম আমি ওর কী ক্ষতি করেছি? কেন ও আমার পিছে লেগেছে?
স্ত্রী এবার স্বামীর বক্তব্যের লাগাম টেনে ধরলো, “উইলিয়াম, আমার মনে হয় আমরা মূল আলোচনা থেকে সরে যাচ্ছি। আলোচনা হচ্ছিল আমাদের ভালোবাসা নিয়ে। সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা যেমন হওয়া উচিত আমাদের ভালোবাসা কখনোই তেমন ছিল না। বরং, আমাদের ভালোবাসা ইন্দ্রিয়সুখের উপলক্ষ হয়েছে মাত্র।”
–কিন্তু সোনা, এই ইন্দ্রিয়সুখের উপলক্ষ না থাকলে আমাদের সন্তানগুলো কীভাবে হত, বলতো? আর তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি না এখানে শুধু ইন্দ্রিয়সুখই কাজ করেছে।
“তুমি বিশ্বাস না করলেই তো আর সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যাবে না। কোন জিনিস কি কখনো একই সাথে সাদা, কালো দুটোই হতে পারে?” প্রশ্নটা করে স্ত্রীর মনে হল স্বামীকে বেশ বেকায়দায় ফেলা গেছে।
স্বামী কিন্তু ঠিকঠাক মত উতরে গেল–“অবশ্যই পারে। তোমার সানশেডের কথা চিন্তা কর, এটার বাইরে কালো আর ভেতরে সাদা।”
এত দ্রুত উত্তর পেয়ে যাবে আশা করেনি স্ত্রী। স্বামীকে নিরস্ত্র করলো সে–“কূটতর্ক কর না।”
–ঠিক আছে করলাম না। কিন্তু লক্ষ্মীসোনা! আমাকে বলোতো, তুমি নিজে মন থেকে কী বিশাস কর? ওটিলিয়ার ওইসব ছাইপাশ বইয়ের মত কথা বল না, নিজের বুদ্ধিকে অন্যের কাছে বিক্রি কর না। প্লিজ, নিজের মত করে চিন্তা কর, আমার লক্ষ্মী বউয়ের মত চিন্তা কর। আমাকে বল, তুমি নিজে তোমার অবস্থান কেমন বলে মনে কর।
–তোমার সম্পত্তি বলে মনে করি। তুমি তোমার পরিশ্রমের বিনিময়ে এই সম্পত্তি কিনে নিয়েছ।
–একদম ঠিক কথা। তুমি আমার সম্পত্তি। ঠিক যেমন আমিও তোমার সম্পত্তি। তোমার একার সম্পত্তি। তোমার স্বামীর ওপর আর কোন মেয়েলোকের কোনও অধিকার নেই। কেউ অধিকার দাবি করলে তুমি নিশ্চয়ই তাকে আস্ত রাখবে না, তাই না? এই সম্পত্তি তোমার স্বামী তোমাকে উপহার দিয়েছে; কিংবা বলা যায়, তোমাকে সম্পত্তি হিসেবে পাবার জন্য সে নিজেকে তোমার সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। আমি কি বোঝাতে পারলাম? এবার কি আমরা থামতে পারি?
দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণের নিরবতা বিরাজ করল। তারপর স্ত্রী আবার হতাশ ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল–“কিন্তু আমরা আমাদের জীবনটা শুধু ক্ষুদ্র জিনিসের পেছনেই ব্যয় করেছি, উইলিয়াম। আমাদের জীবনের। কখনোই কোনো মহান উদ্দেশ্য ছিল না।”
–কে বলেছে ছিল না? অবশ্যই ছিল এবং আছে। আমরা সবসময় এমন হেসেখেলে সময় পার করিনি; অনেক কঠিন সময় পার করতে হয়েছে। চিন্তা করে দেখ, আমরা কি আমাদের প্রজাতিটিকে টিকিয়ে রাখতে নতুন প্রজন্মের জন্ম দিইনি? এদের জন্ম দিতে গিয়ে চারবার তোমাকে মৃত্যুঝুঁকি নিতে হয়েছে, এদের ঘুম পাড়ানোর জন্য তোমার নিজের রাতের ঘুম চুরি গেছে, দেখাশোনা করার জন্য মাটি হয়েছে দিনের আনন্দটুকুও। এদের খাওয়াতে গিয়ে আমরা নিজেরা না খেয়ে থেকেছি, কঠিন থেকে কঠিনতর পরিশ্রম করেছি। আমাদের এই ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়েই তো এরা বড় হয়ে উঠছে, তাই না? আমরা স্বপ্ন দেখি, ওরা একদিন আদর্শ নারী আর পুরুষে পরিণত হবে। ভেবে দেখতো, আমরা যদি কোন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সন্তানদের জন্য এই ত্যাগগুলো স্বীকার না করতাম, তাহলে। কি আজ আমাদের ছয় রুমের অভিজাত একটা ফ্ল্যাট থাকতে পারত না? সেই ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দেয়ার জন্য থাকত দারোয়ান, সিল্কের কাপড় আর মণিমুক্তার দামী গহনা পরে তুমি ঘুরে বেড়াতে পারতে; আমাকেও দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হত না, হয়ত তোমাকে নিয়েই সারাক্ষণ মেতে থাকতে পারতাম। কিন্তু তা না-করে আমরা এভাবে কষ্ট সহ্য করছি শুধুমাত্র আমাদের ভালোবাসার ওপর আস্থা রেখেইতো, তাই না? একে কি কোনভাবে পুতুলের সংসারের সাথে তুলনা করা যায়? নাকি সেটা ঠিক? ওই অবিবাহিতা বুড়ি মহিলারা যেভাবে চিন্তা করে আমরা কি আসলেই তেমন স্বার্থপর? ওদের কথায় কি আসলেই অতটা গুরুত্ব দেয়া উচিত, বলো তো? একবার চিন্তা করে দেখ–কেন? কিসের আশায় এত এত মহিলা অবিবাহিত থাকছে? কেউ যখন ওদের বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন ওদের গর্বের সীমা থাকে না, অথচ ভাব দেখায় এমন যেন বিয়ে না করে বিরাট আত্মত্যাগ করে ফেলেছে! আর মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ল্যাটিন শেখার কথা বলছিলে তো? বড় গলার জামা পরে পরহিতকর কাজ করার নামে, নিজের সন্তানদের অবহেলিত রেখে ঘর ছেড়ে যাওয়াটা কোনভাবেই মহান উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোন কাজ হতে পারে না; বরং, দায়িত্ববোধের চরম অভাব থাকলেই এমনটা হতে পারে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের জীবনের লক্ষ্য ওই ওটিলিয়ার লক্ষ্যের থেকে অনেক মহান। আমি বিশ্বাস করি, আমরা এমন শক্ত-সমর্থ, যোগ্য পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে যাবো যারা আমাদের ব্যর্থতাগুলোকে সফলতায় পরিণত করবে। আর এতে যে আনন্দ, সেটা ওটিলিয়া কখনোই বুঝবে না। ওর ল্যাটিন ওকে এক্ষেত্রে কোন সহযোগিতাই করতে পারবে না। যাহোক, অনেক কথা বলে ফেললাম, আমাকে আবার জাহাজে ফিরতে হবে। তুমি কি আমার সাথে উঠবে গুরলী?
স্ত্রী কোন উত্তর না-করে আগের মতই পাথরের পাশে বসে রইল। অতএব স্বামী একাই রওনা দিতে উদ্যত হলেন। তাঁর পদক্ষেপ আজ একটু বেশিই ভারি মনে হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে প্রকৃতিও যেন তাল মিলিয়ে ভারি হয়ে এল, নীল সমুদ্রের বুকে অন্ধকার নামল, সূর্যের উজ্জ্বলতাও নিভে এল। হাঁটতে শুরু করলেও স্বামীর মন কিন্তু ওই পাথরের পাশেই পড়ে ছিল। নিজেকে তিনি অনবরত প্রশ্ন করতে লাগলেন–“এ তুমি কোথায় যাচ্ছ, উইলিয়াম? কেন যাচ্ছ?” কবরস্থানের পাশের বেড়া অতিক্রম করার সময় তাঁর বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল–ওহ্! আমি যদি ওইখানে ওই পাথরের পাশেই সারাজীবন শুয়ে থাকতে পারতাম, ওইখানেই যদি আমার কবর হত, কবরের পাশে কাঠ দিয়ে ক্রুশ বানানো থাকত। কিন্তু আমি জানি, ওকে ছাড়া সেই কবরে শুয়েও আমি সুখ পেতাম না! ওহ্! গুরলী! গুরলী!
*** *** ***
সবকিছুতে একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, আম্মা!
কথাগুলো নিজের শাশুড়িকে বলছিলেন ক্যাপ্টেন সাহেব। শরতের এক কনকনে ঠাণ্ডা সকালে শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি।
–সমস্যাটা কী, উইলি? তোমাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।
–সমস্যা, সমস্যা যে কী তা-ই তো বুঝতে পারছি না। গতকাল ওরা বাড়িতে দেখা করেছে, তার আগের দিন দেখা করেছে প্রিন্সেস রেস্টুরেন্টে। ওদিকে ছোট মেয়েটা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। খুব খারাপ লাগছিল, তবুও গুরলিকে কিছু বলিনি–হয়ত ভেবে বসবে ওর বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে ইচ্ছে করেই আমি এসব করছি। ওহ্! কেউ যদি বিশ্বাসই হারিয়ে ফেলে…
শেষের কথাগুলো তিনি আর শেষ করতে পারছিলেন না, বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ থেমে আবার শুরু করলেন,
–নৌ আদালতে আমার এক বন্ধু আছে। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ যদি বেশি-বেশি তামাকের গন্ধ দিয়ে তাঁর স্ত্রীর বান্ধবীকে মেরে ফেলে তবে তা সুইডিস আইনে বৈধ কি না? ও জানাল, এমন কোন কিছুর বৈধতা আইনে নেই, আর থাকলেও সেটা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ, তাতে হিতে-বিপরীত হবার সম্ভাবনা আছে। তবে ভাগ্য ভালো যে, আমার বন্ধুটি স্ত্রীর বান্ধবীর পক্ষে কোন কথা বলেনি; বললে ঘাড় ধরে ওকে জানালা দিয়ে ফেলে দিতাম! উফ! চারদিকে সমস্যা, কী যে করি!
ক্যাপ্টেনের শাশুড়ি বিজ্ঞের মত মাথা নাড়লেন–“হুম, ভাববার বিষয়। কিন্তু তুমি এত ভেঙে পড়ো না, উইলি। একটা-না-একটা উপায় আমরা ঠিকই খুঁজে বের করব। এভাবে তো আর চলতে দেয়া যায় না, তুমিতো একেবারে ব্যাচেলরের মত জীবন যাপন করছ!”
–না, আমিও আর পারছি না। প্রতি পদক্ষেপে এতকিছু হিসাব করে চলাটা কারো পক্ষেই সম্ভব না। আমি যতটা সম্ভব সহজ করে ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি, তবুও কীভাবে কীভাবে যেন সমস্যা হয়েই যায়! এইতো কয়েকদিন আগে ওকে বললাম, “জীবনযাত্রায় পরিবর্তন না আনলে কিন্তু তোমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে।” আমি বেশ আন্তরিকভাবেই কথাটা বলেছিলাম।
–আচ্ছা! তা, এরপর গুরলী কী বলল?
–বলল, “তুমি যখন জাহাজে থাকো, তখন তুমি যেভাবে খুশি সেভাবে চলাফেরা কর, কর না? নিজের শরীরের ওপর তোমার পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব, আমারও নিজের শরীরের ওপর পূর্ণ অধিকার আছে।”
কী চমৎকার তত্ত্ব! আমি আর পারছি না আম্মা। দুঃখে আমার চুল পেকে যাচ্ছে!
–হুম, সমস্যা আসলেই ভয়াবহ। তবে উপায় কিন্তু একটা আছে, যেকোনভাবে গুরলীর মনে তোমাকে নিয়ে হিংসা ঢুকিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধিটা পুরনো হলেও বেশ কার্যকর। এতে হয় অবস্থার চরম বিপর্যয় ঘটবে, নয়তো পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে। তবে আশার কথা হচ্ছে, ওর মনের মধ্যে যদি তোমার জন্য ছিটেফোঁটা ভালোবাসাও থাকে, তবে এই পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত তোমার উপকারই হবে।
–আছে আম্মা! ভালোবাসা আছে। অবশ্যই আছে, আমি জানিতো। ভালোবাসা এত সহজে মরবার জিনিস নয়।
ক্যাপ্টেনের শাশুড়ি চেয়ার টেনে কাছাকাছি এসে বসলেন, “তাহলে শোন, তোমাকে ওটিলিয়ার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে হবে।”
–প্রেমের অভিনয়! তাও আবার ওটিলিয়ার সঙ্গে? ওই ডাইনিটার সঙ্গে?
–ওহহো, বুঝতে চেষ্টা কর, তুমিতো আর সত্যি সত্যি প্রেম করছ না। যা করছ সেটা নিজেদের ভালোর জন্যই করছ। এখন মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করে দেখতো, তোমার এমন কোন বিষয়ে দক্ষতা আছে কি না যেটা ওটিলিয়ার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।
–দক্ষতা? ক্যাপ্টেন চোখ বুজে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, “…হ্যাঁ, পেয়েছি। আজকাল ওদের প্রায়ই পরিসংখ্যান নিয়ে কথা বলতে শুনছি। মানে, কতভাগ নারী পতিত হয়েছে, কতভাগ হতভাগ্য, কতভাগ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত, এইসব আরকি! তো, কোনভাবে যদি ওদের এই আলোচনাটাকে গণিতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় তাহলে আমার সুবিধে হবে। গণিতে আমার বেশ মাথা খোলে।”
শাশুড়ি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, “এইতো! তাহলে গণিত দিয়েই শুরু হোক। একটু একটু করে এগুতে হবে। যেভাবে ঘাড়ের ওপর দিয়ে চাদর দিয়ে শেষমেষ পুরো শরীরটাকে পেচিয়ে ফেলতে হয়, ঠিক সেভাবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওটিলিয়াকে তোমার বাড়িতে আসার নিমন্ত্রণ দাও, ওর সুস্বাস্থ্য কামনা করে একসাথে মদ পান কর, তারপর জড়িয়ে ধরে চুম্বন কর। প্রয়োজনমত তুমি একটু-আধটু বাড়াবাড়িও করতে পারো; বুঝতেই পারছ আমি কী বলতে চাচ্ছি! তবে খেয়াল রাখতে হবে, পুরো ব্যাপারটা যেন গুরলীর চোখের সামনে হয়। চিন্তা কর না, শুরুর দিকে গুরলী এসব নিয়ে রাগ করবে না; এ ব্যাপারে তুমি আমার ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারো। যাহোক, এভাবে একসময় ওটিলিয়ার সঙ্গে আরও জটিলতর গাণিতিক বিষয়ে কথা বলতে শুরু কর। এমন জটিল যেন গুরলীর সেখানে অংশগ্রহণ করার কোন সুযোগ না থাকে; ওকে শুধু বসে বসে দেখে যেতে হয়, বুঝলে? আপাতত এটুকু করে সামনের সপ্তায় আমার সঙ্গে আবার দেখা করে ফলাফল জানিয়ে যেও।”
শাশুড়ির সঙ্গে শলাপরামর্শ করে, পরিকল্পনা গোছাতে-গোছাতে বাড়ি ফিরলেন ক্যাপ্টেন সাহেব। বেশ কিছু আদি রসাত্মক বইপত্র পড়ে ওটিলিয়ার সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ের বুদ্ধিটাকে ভালো করে শানিয়ে নিলেন। এবার অভিযান শুরুর পালা…
*** *** ***
এক সপ্তাহ পর ক্যাপ্টেনকে আবার শাশুড়ির বাড়িতে দেখা গেল। আজ বেশ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে তাকে। ভীষণ উচ্ছ্বাস নিয়ে গ্লাস ভরে ‘শেরী’ পান করছেন। সবকিছু মিলিয়ে ক্যাপ্টেন যেন আজ এক নতুন প্রাণে টগবগ করছেন। তাঁর বৃদ্ধা শাশুড়ি কপালের ওপর চশমা তুলে বললেন, “এবার বিস্তারিত বল।”
ক্যাপ্টেন সাহেব শুরু করলেন–শুরুতে কাজটা একটু জটিল মনে হচ্ছিল, কারণ, ওটিলিয়া আমাকে বিশ্বাসই করতে চাচ্ছিল না। ভেবেছিল, আমি বোধহয় ওকে নিয়ে ঠাট্টা করছি। যাহোক, কিছুক্ষণ পর আমি বেশ কায়দা করে একটা পরিসংখ্যানের কথা বললাম। আমেরিকানদের নৈতিকতার ওপর করা একটা সম্ভাব্য হিসাব নিয়ে বলতে শুরু করলাম। এ হিসেবের ফল কী হয়েছিল সেটা বলতে গিয়ে বেশ একটু ধোঁয়াশা সৃষ্টি করলাম। তারপর খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে বললাম, এই পরিসংখ্যানের ফলাফল রীতিমত নতুন এক যুগের সৃষ্টি করেছিল। ওটিলিয়ার এ ব্যাপারে কোন ধারণা না-থাকলেও ব্যাপারটা ওর মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে বোঝা গেল। আমিও সুযোগ কাজে লাগালাম। নানারকম উদাহরণ দিয়ে, ছবি এঁকে বোঝালাম, কত ভাগ নারীর পতিত হবার সম্ভাবনা আছে সেটা সম্ভাব্যতার
কিছু সূত্র প্রয়োগ করে খুব সহজেই দেখিয়ে দেয়া সম্ভব। এইবেলা ওকে একটু বিস্মিত মনে হল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর উৎসাহ বেড়ে চলেছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পরদিন ও আবার দেখা করতে রাজি হল। ওদিকে, ওটিলিয়ার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হচ্ছে দেখে গুরলীকেও ভীষণ খুশি মনে হল। খুশি হয়ে ও যে কাজগুলো করল সেগুলো আমার পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে অনেকটা কাজে এল–ওটিলিয়াকে আমার রুমে পাঠিয়ে দিয়ে দরজা টেনে দিয়ে গেল গুরলী! আমরা ওই রুমেই সারা বিকেল কাটালাম। নানা হিসেবপাতি করলাম। ডাইনিটাকে খুব খুশি মনে হচ্ছিল। ও বোধহয় ভাবছিল, আমাকে বেশ পোষ মানানো গেছে। যাহোক, প্রায় তিন ঘণ্টা কাজ করার পর আমরা খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম! রাতে খাবার টেবিলে বসে গুরলী দেখলো আমরা পুরনো বন্ধুদের মত একে অপরকে খ্রিস্টান নাম ধরে ডাকছি। ব্যাপারটায় আরেক প্রস্থ রং চড়ালাম আমার পুরনো শেরীর বোতল বের করে এনে খুব ঘটা করে এই মুহূর্তটাকে উদযাপন করলাম। তারপর… তারপর আমি ওর ঠোঁটে চুম্বন করলাম। ওহ! ঈশ্বর যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করেন। গুরলী শুরুতে একটু হকচকিয়ে গেলেও রাগ করল বলে মনে হল না। বরং, একটু যেন খুশিই মনে হল।
শেরীটায় বেশ ঝাঁঝ ছিল। ওটিলিয়ার পক্ষে অতটা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও একেবারে নেতিয়ে পড়ল। আমি ওকে ওর কোট দিয়ে ভালো করে জড়িয়ে বাড়িতে দিয়ে আসার জন্য উঠলাম। যাবার সময় আলতো করে ওর হাত ধরে এগুচ্ছিলাম আর আকাশের বিভিন্ন তারকাদের নাম বলছিলাম। এ ব্যাপারেও ওর আগ্রহ আছে দেখা গেল। ছোটবেলা থেকেই ও নাকি তারকা দেখতে পছন্দ করে, কিন্তু কখনোই সেগুলোর নাম মনে রাখতে পারে না। অবশ্য এমন নচ্ছার মহিলারা কোন বিষয়েই ভালো করে কিছু জানতে পারে না; কেবল পুরুষ মানুষের দোষ খুঁজে বেড়াতেই সময় চলে যায়। যাহোক, ওর আগ্রহ বাড়তেই থাকলো। ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় এমনভাবে বিদায় নিলাম যে, কেউ দেখলে ভাববে আমরা হয়ত অনেক দিনের পুরনো বন্ধু কিন্তু মাঝে কিছুদিন ভুল বোঝাবুঝির কারণে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না!
পরদিন আবারও বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। রাতের খাবারের আগ পর্যন্ত আমরা একসাথে কাজ করলাম। মাঝে দু’একবার গুরলী এসে ‘হুঁ’, ‘হ্যাঁ’ করে গেল। খাবার টেবিলেও আমরা গণিত আর তারকা বিষয়ক কথাবার্তা বললাম। আমি ইচ্ছে করে এমন সব জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম যে, গুরলীর কিছুই বলার ছিল না, ও। চুপচাপ শুধু আমাদের কথা শুনে যাচ্ছিল। খাওয়া শেষে আগের দিনের মতই ওটিলিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলাম। ফেরার পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা করলাম। দুজন মিলে গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে ‘পাঞ্চ’ পান করলাম। বাড়ি ফিরতে রাত একটা বেজে গেল। গুরলী তখনো জেগে ছিল, আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বাড়ি পৌঁছামাত্র গমগমে গলায় জিজ্ঞেস করল, “এতক্ষণ কোথায় ছিলে, উইলিয়াম?” আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল, বললাম–“আমাদের একে-অন্যকে এত বেশি কথা বলার ছিল যে, অন্য সবকিছু ভুলেই গিয়েছিলাম।” এইবার মনে হল ওষুধে ধরেছে। গুরলী আগের চেয়েও থমথমে গলায় বলল, “অর্ধেক রাত পর্যন্ত কোন মহিলার সাথে বাইরে কাটানোটা কোন ভাল কাজ বলে আমার মনে হয় না।” আমি একটু অস্বস্তিতে পরার ভান করলাম। তারপর, তোতলাতে তোতলাতে বললাম, “একজন মানুষের যদি অন্য একজন মানুষকে এত বেশি কথা বলার থাকে তাহলে কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা না, তা খেয়াল থাকে না।” গুরলী এবার ঠোঁট বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “তা দুনিয়ার কোন মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তোমরা এতক্ষণ কথা বললে?” আমার অভিনয়টাকে আর একটু জমিয়ে নিয়ে বললাম, “তা তো মনে নেই!”
ক্যাপ্টেনের শাশুড়ি এবার একটু দম নিলেন। “হুম, ভালোই ম্যানেজ করেছ দেখা যাচ্ছে। তারপর কী হল?”
ক্যাপ্টেনও একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলেন–
তৃতীয় দিন আমরা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সময় গুরলী ওর সেলাইফোঁড়াই এর কাজ নিয়ে আমাদের পাশে এসে বসল। আমাদের আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানে বসেই কাজ করল। রাতে খাবার টেবিলে আগের দু’দিনের মত অতটা আনন্দফুর্তি না হলেও জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনাটা ঠিকঠাকমতই হল। বেরুবার সময় আমি ডাইনিটার গামবুটের ফিতা বেঁধে দিলাম। ব্যাপারটা গুরলী বেশ বাঁকা চোখে দেখল বোঝা গেল। বুট পরা শেষে উঠে দাঁড়িয়ে শুভরাত্রি বলার সময় ডাইনিটা আমার দিকে গাল এগিয়ে দিল। গুরলী যে মনে মনে রাগে। জ্বলছিল বাইরে থেকেও সেটা আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। যাহোক, যথারীতি ডাইনিটাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য হাত ধরে সাথে নিয়ে বের হলাম। পথে যেতে যেতে মৃতদের আত্মার শান্তি নিয়ে কথা বললাম। দেখা গেল এ বিষয়েও ডাইনিটার আগ্রহ এবং হতাশা আছে। আমি বলতে। থাকলাম, “জানো তো, তারকাদের মধ্যেই আত্মারা বসবাস করে।”
ফেরার পথে একা একাই এ্যান্ড হোটেলে গেলাম, খানিকটা পাঞ্চ’ পান। করলাম। তার পর, রাত দুটোর দিকে হেলতে-দুলতে বাড়ি ফিরলাম। গুরলী তখনও জেগেছিল। আমি দেখেও না-দেখার ভান করে সোজা আমার। রুমে চলে গেলাম। গুরলী তো বেশ কিছুদিন যাবতই আমার সঙ্গে থাকা বন্ধ করে দিয়েছিল। অতএব, ব্যাচেলরের মতই আমি একা একা ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। গুরলী আজ আমাকে কোন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করল না।
পরদিন ওটিলিয়াকে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে বিশদভাবে বোঝাতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর গুরলী এসে ঘোষণা করল, জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপারে সে ব্যাপক আগ্রহী; অতএব সে-ও আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়। কিন্তু ওটিলিয়া আপত্তি করল; বলল, আমরা ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি, গুরলী এখন কিছুই বুঝবে না; বরং আমরা যখন আলোচনাটা শেষ করবো, তখন সে গুরলীকে প্রাথমিক বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেবে। গুরলী এতে ভীষণ বিরক্ত হল। রাগে গজগজ করতে-করতে বেরিয়ে গেল। রাতে আমরা অনেকটা ‘শেরী’ পান করলাম। এমন সুন্দর একটা সন্ধ্যা উপহার দেবার জন্য ওটিলিয়া যখন ধন্যবাদ জানালো, তখন আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলাম। সাথে সাথে গুরলী যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যখন ওটিলিয়ার গামবুটের ফিতা বেঁধে দিলাম তখন… তখন…
শাশুড়ি বুঝতে পারলেন, কিছু একটা বলতে গিয়ে ক্যাপ্টেন লজ্জা পাচ্ছে। মেয়ের জামাইয়ের অস্বস্তি ভাঙাতে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে বললেন, “আমার কাছে লজ্জার কিছু নেই, বাবা! আমি নিতান্তই বুড়ি মানুষ।”
ক্যাপ্টেন হো হো করে হেসে দিলেন! না-না, আম্মা! আমি অতটা খারাপ না। আপনার সাথে একটু মজা করছিলাম। যাহোক, ওভারকোট পরতে গিয়ে তো আমি রীতিমত চমকে উঠলাম। দেখি আমার আগেই কাজের মেয়েটা রেডি হয়ে ওটিলিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার পায়তারা করছে। গুরলীকে দেখলাম ওটিলিয়াকে বলছে, গতকাল সন্ধ্যায় বাইরে থেকে আমার নাকি ঠাণ্ডা লেগেছে। তাই তার ভয় হচ্ছে, আজকে রাতে বাইরে বের হলে হয়ত আরও খারাপ কিছু হতে পারে, সেজন্য কাজের মেয়েটাই আজ ওটিলিয়াকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ব্যাপারটা বোধহয় ওটিলিয়ার আত্মসম্মানে লাগল। কিছু না বলে একা একাই গটগট করে হেঁটে চলে গেল।
পরের দিন বারোটার সময় কলেজে নিয়ে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার কতগুলো যন্ত্রপাতি দেখাবো বলে ওটিলিয়াকে কথা দিয়েছিলাম। ও সময়মতই এল; কিন্তু কোন কারণে ভীষণ বিষণ্ণ লাগছিল ওকে। বেশ কয়েকবার নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, ও নাকি বাড়িতে গিয়েছিল গুরলীর সাথে দেখা করতে; কিন্তু গুরলী খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। অথচ, সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না গুরলী কেন এমন করল।
রাতে খাবার টেবিলে গুরলীর মধ্যে একটা বিশাল পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। দেখে মনে হল, যেন মরা মাছের মত ঠান্ডা হয়ে পরে আছে। বুঝলাম ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু আমার জন্য তো এটাই মোক্ষম সুযোগ। অতএব, গলায় রাগ ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি ওটিলিয়াকে কী বলেছ? ও খুবই কষ্ট পেয়েছে।”
–আমি ওকে কী বলবো? ওকে আমার কী-ই-বা বলার আছে? শুধু বলেছি, ও একটা নষ্টা মহিলা।
–ছিঃ! তুমি এমন কথা বলতে পারলে? তুমি নিশ্চয়ই ওকে হিংসা করছ না, তাই না?
এতক্ষণ খুব কষ্টে নিজেকে সংযত করলেও এবারে রাগে ফেটে পড়ল গুরলী–“হ্যাঁ করছি, ওকে হিংসা করছি আমি।”
–আমারও অবশ্য সেরকমই মনে হচ্ছিল, আর সেটাই সবচেয়ে বেশি অবাক লাগছে। কারণ, আমি নিশ্চিত, ওটিলিয়ার মত অমন বুদ্ধিমতী বিচারবোধসম্পন্ন মহিলার কোনভাবেই অন্য মহিলার স্বামীকে নিয়ে কোন বদ মতলব থাকতে পারে না।”
–না, তা পারে না। কিন্তু অন্য মহিলার স্বামীর তো তাকে নিয়ে কোন বদ মতলব থাকতে পারে।
হা হা হা… এরপর মজার ব্যাপার কী হল জানেন, আম্মা? এতদিন আমি ওটিলিয়াকে নিয়ে যেমন ভাবতাম এবার গুরলী সেভাবে ওটিলিয়ার ওপর রাগ ঝাড়তে লাগল; আর এতদিন গুরলী যেভাবে ওটিলিয়ার পক্ষ নিত এবার আমি সেভাবে ওটিলিয়ার সাফাই গাইতে লাগলাম। এভাবেই চলল বেশ কিছুক্ষণ।
সেদিন সন্ধ্যায় ওটিলিয়া এল না, একটা চিঠি পাঠালো। না আসার জন্য চিঠিতে নানারকম অজুহাত দেখিয়েছে সে; সেই সঙ্গে ইঙ্গিত করেছে যে, সে বুঝতে পেরেছে সে এখন আর কারো কাছে কাক্ষিত নয়। আমি প্রতিবাদ করলাম। বললাম, আমার গিয়ে ওটিলিয়ার রাগ ভাঙিয়ে ওকে নিয়ে আসা উচিত। এবার গুরলীর মধ্যে বুনো উন্মত্ততা ভর করল। ও এতক্ষণে নিশ্চিত, আমি ওটিলিয়ার প্রেমে পড়েছি; যে-কারণে ওকে আর পাত্তা দিচ্ছি না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে কান্নাই করে দিল বেচারি। কাঁদতে কাঁদতে নানা দুঃখ করতে লাগল। বলল, সে বুঝতে পেরেছে, সে একটা বোকা মেয়ে যে কিছুই বোঝে না, কিছুই পারে না আর… আর, গণিত জানে না! এতক্ষণে আমি বুঝে গেলাম, পাখি আমার আগের ঠিকানায় ফিরেছে। অতএব… স্লেজ গাড়ি ডাকলাম, ঘুরে বেড়ালাম, হোটেলে গিয়ে গরম গরম মদ পান করলাম, আর রাতের বেলায় ছোট্ট একটা টেবিলে বসে একসাথে খেলাম। মনে হল, যেন আজ আমাদের আবার নতুন করে বিয়ে হল। এরপর কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।
“তারপর?” ক্যাপ্টেনের শাশুড়ি চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে চোরা হাসি হাসলেন।
–তারপর? তারপরের কথাতো আর আপনাকে বলা যাবে না!
–আচ্ছা, বেশ। তা, তার পরে কী হল?”
তার পর? তার পর, যেহেতু সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, আমরা সন্তানদের লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করলাম। কীভাবে ওদেরকে যাবতীয় কুসংস্কার আর ফালতু চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে রেখে সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করা যায় তা নিয়ে কথা বললাম। ঠিক করলাম–যখন আমরা একসঙ্গে থাকবে শুধুমাত্র তখনই এসব নিয়ে আলোচনা করব; একাকী কিংবা অন্য কারো সঙ্গে এসব নিয়ে কখনো কথা বলব না, কারণ তাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে। কী বলেন আম্মা, ঠিক বলেছি না?
–আমি আর কী বলবো! যা বলার তোমাদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়েই বলবো।
–অবশ্যই, অবশ্যই দাওয়াত খেতে আসবেন। আপনি সেখানে পুতুলের নাচ দেখতে পাবেন, ছোট্ট পাখির গান শুনতে পাবেন, আরও শুনতে পাবেন কাঠঠোকরার কিচিরমিচির। আপনি এমন একটা ঘর দেখতে পাবেন যার ছাদ পর্যন্ত সুখ দিয়ে ঠাসা। কারণ সে ঘরে কেউ রূপকথার অলৌকিকতার অপেক্ষায় বসে থাকে না, সে-ঘরে সবাই ভালোবাসা দিয়েই সব শিখিয়ে দেয়। সে ঘরে আপনি সত্যিকারের একটা পুতুলের সংসার দেখতে পাবেন।
ক্ষতিপূরণ
কলেজের সবাই ‘জিনিয়াস’ বলে জানত। একদিন যে নিজেকে আলাদা করে চেনাবেই সে ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করার পর ছেলেটি স্টকহোমে ফিরে যেতে বাধ্য হল। সেখানে জাহাজ জেটিতে কাজ নিতে হলো। ডক্টরেট ডিগ্রি পাবার জন্য যে গবেষণা-প্রবন্ধ তৈরি করছিল, সেই কাজও আপাতত বন্ধ রাখতে হলো। কামাই-রুজির বন্দোবস্ত খুব একটা ভালো না-হলেও মনে মনে সে ভীষণ উচ্চাভিলাষী। চিন্তা করে দেখলো, এই উচ্চাভিলাষ বাস্তবায়নে বিয়ে করাটা খুব কাজে দেবে। কারণ, যুতসই একটা বিয়ে করতে পারলে টাকা-পয়সার জন্য আর ফিরে তাকাতে হবে না। তাই সে বেছে বেছে নামী-দামী পরিবারগুলোর সঙ্গেই বেশি খাতির জমাতো। উপছালা (এখানে সে আইনে পড়েছে) এবং স্টকহোম দু জায়গাতেই তার একই রকম পরিকল্পনা ছিল। উপছালায় পড়াকালীন সব সময় সে তক্কে তক্কে থাকতো কারা নতুন ভর্তি হল। কোন অভিজাত ঘরের সন্তান ভর্তি হবার খবর পাওয়ামাত্র তার সঙ্গে ভীষণ ভাব জমিয়ে ফেলত। সেই অভিজাত সন্তানটিও খুব শীঘ্রই তার চাটুকারিতাকে পছন্দ করতে শুরু করত। এভাবে অনেকের সাথেই তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রয়োজন মেটানোর মত সুসম্পর্ক। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে এসব অভিজাত বন্ধুদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেত।
এই গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার উপলক্ষটা ছিল উদ্দেশ্য পূরণের একটা মোক্ষম সুযোগ। প্রকৃতিগতভাবেই ওর মধ্যে সব ধরনের সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছিল। সবার সঙ্গে খুব সুন্দর করে মিশতে পারত, গানের গলাও ছিল চমৎকার। বিভিন্ন খেলাধুলায় পারদর্শিতার পাশাপাশি মেয়ে পটানোর কাজটাও বেশ ভালোই জানা ছিল। ফলে নারীমহলে ও ছিল এক জনপ্রিয় চরিত্র। পকেটের অবস্থা যা-ই-হোক না কেন, কাপড়-জামা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। দামী পোশাকআশাক পড়ে ফুলবাবুটি সেজে চলাফেরা করত! অবশ্য, এজন্য ও কখনোই বন্ধুবান্ধব বা অন্য কারো থেকে টাকা ধার করত না। কীভাবে কীভাবে যেন ম্যানেজ করে ফেলত। নিজের। ফুটানি জাহির করার সম্ভাব্য সবগুলো উপায়ই ও ব্যবহার করত। যেমন, হয়ত খুব আজেবাজে দুটো কোম্পানির শেয়ার কিনল, তারপর যখনই সুযোগ পাবে তখনই বলে বেড়াবে যে, তাকে শেয়ারহোল্ডারদের বাৎসরিক মিটিংয়ে যেতে হবে!
গত দু’বছর যাবত ছেলেটিকে এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের পেছনে সময় দিতে দেখা যাচ্ছে। মেয়ের বাপের টাকা-পয়সা বিস্তর, এবং সেগুলো হস্তগত করাটাই যে তার প্রধান উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু হঠাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল! যাবতীয় জাঁকজমক থেকে হুট করে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল ছেলেটা। কিছুদিন পর জানা গেল, এক দরিদ্র কুমোরের মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক হয়েছে, এমনকি বাগদানও হয়ে গেছে। বন্ধুরা কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারল না। ওর মত উচ্চাভিলাষী ছেলে কীভাবে এ-কাজ করল তার কোন আগাপাছতলা খুঁজে পেল না। তারা–“ওর সব পরিকল্পনাইতো গোছালো ছিল। ও এত সূক্ষ্ম চাল চেলে এগুলো যে সাফল্য ধরা দেয়া শুধু কটা দিন সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র। চামচে খাবার তুলে নেয়া হয়েছে, এখন শুধু সেটা গলাধঃকরণ বাকি, অথচ…!” অবশ্য ও নিজেও বুঝতে পারল না কীভাবে কী হয়ে গেল। স্টিমারে ফেরার সময় ছোটখাটো একটা মেয়েকে দেখে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল, এতদিনের পরিকল্পনা সব ভেস্তে গেল। মেয়েটাকে দেখার পর। থেকেই মনে হচ্ছিল, কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। যাহোক, নিজেকে প্রবোধ মানানোর জন্যই হয়ত বন্ধুদের। জিজ্ঞেস করল, “তোদের মনে হয় না মেয়েটা সুন্দরী?”
বন্ধুরা অকপটে স্বীকার করল, তাদের সে রকম কিছু মনে হয়নি!
“কিন্তু ও ভীষণ বুদ্ধিমতী। একবার ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখিস, ওর চোখের তারায় এক দুর্বোধ্য অভিব্যক্তি চোখে পড়বে তোদের!”
বন্ধুরা এবারেও তাকে হতাশ করল। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের বিশেষ কিছু মনে হয়নি। আর, বুদ্ধির কথা বলা যাচ্ছে না; কারণ তারা কখনোই মেয়েটিকে মুখ খুলতে দেখেনি!
তবে, বন্ধুরা যা-ই বলুক, প্রতি সন্ধ্যায়ই ছেলেটি কুমোরের বাড়িতে হাজির হয়। কুমোর ব্যাটা ভারী চালাক, কখন কাকে মত দিয়ে ফেলে বলা শক্ত। সন্ধ্যাগুলো তাই কুমোরের পরিবারের সাথেই কাটে–ভালোবাসাকে হারাতে দেবে না সে। আশেপাশে কেউ না-থাকলে, মেয়েটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রেম নিবেদন করে। এ অভ্যাস অবশ্য আগে থেকেই তার রপ্ত করা ছিল। তবে, এসবের বাইরেও মেয়েটাকে খুশি করার জন্য সে নানারকম চেষ্টা করে–মেয়েটার সুই-সুতো নিয়ে খেলা করে, গান শোনায়, ধর্মীয় নানা কাহিনি বলে, নাটকের গল্প শোনায়। আর, এ সবকিছুতেই সে মেয়েটার চোখে মৌনসম্মতি দেখতে পায়। ফলে তার উচ্ছ্বাস আরও বেড়ে যায়–মেয়েটাকে ভালোবাসার কবিতা লিখে উপহার দেয়, পড়ে শোনায়। আর… আরও অনেককিছু। এভাবেই ধীরে ধীরে ছেলেটি তার ভালোবাসার মন্দিরে নিজের গর্ব, অহংকার, বোধ, উচ্চাভিলাষ সবকিছু উৎসর্গ করল, এমনকি নিজের গবেষণা-প্রবন্ধটিও। কিছুদিন পর তাদের বিয়ে হল।
বিয়ের দিন কুমোরের খুশি যেন আর ধরে না। গলা অব্দি মদ পান করল। মদ্যপ অবস্থায় নারীজাতি সম্পর্কে নানা অশালীন মন্তব্য, আর চটুল রসিকতা করে এক বক্তৃতা দিল। কুমোরের জামাই কিন্তু তাতে মোটেও অসন্তুষ্ট হল না। সে বরং এগুলোকে একরকম সহজ-সরল, খোশমেজাজি আচরণ বলে ধরে নিয়ে শ্বশুরকে আরও প্ররোচিত করতে থাকল। তার মনে হল, এই সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে নিজেকে আজ খুব হালকা লাগছে।
ওদিকে বন্ধুরা বলল–“ভালোবাসা, এরই নাম ভালোবাসা! ভালোবাসায় সবই সম্ভব!”
*** *** ***
এতদিনে দুজন-দুজনার। আর কোন দূরত্ব বা বাধা নেই। এক মাস গেল, দু’মাস গেল। সময় যে কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে তার কোন গাছ-পাথর নেই…
ছেলেটি খুশিতে আত্মহারা–কী ছেড়ে কী করবে তা-ই ভেবে পায় না। সন্ধ্যার সময়টা দুজন একসাথে কাটায়। ছেলেটি মেয়েটিকে গান গেয়ে শোনায়, মেয়েটির প্রিয় ‘বুনো গোলাপ ফুলের গান। গান শেষ হলে ধর্মকাহিনি আর নাটকের গল্প বলে। মেয়েটি বেশ আগ্রহ নিয়ে সব গল্প শোনে। কিন্তু কখনোই কোন মন্তব্য করে না। চুপচাপ শুনে যায়, আর কাপড়ের ওপর সুঁই-সুতোয় ফুল তোলে।
বিয়ের তৃতীয় মাসে স্বামী-স্ত্রীর অভ্যাসে খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল–স্বামী তার বিকেলবেলা ঘুমানোর পুরনো অভ্যাসে ফেরত গেল। স্ত্রীর কিন্তু একা থাকতে মোটেই ভালো লাগে না, স্বামীর পাশে বসে খুঁটখাঁট করে। স্বামী তাতে খানিকটা বিরক্তই হয়। নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলো গুছানোর জন্য কিছুটা একাকীত্ব প্রয়োজন তার। স্ত্রী মাঝে মাঝে স্বামীর অফিস ফেরার পথে দাঁড়িয়ে থাকে। এ সময়টা তার খুব গর্ব হয়। সহকর্মীদের ছেড়ে, রাস্তা পার হয়ে এসে স্বামী তার হাত ধরছে, এই চিন্তাটা ভীষণ আনন্দ দেয়। বিজয়িনীর বেশে স্বামীকে নিয়ে বাড়ি ফেরে।
চতুর্থ মাসে স্ত্রীর প্রিয় গানটার ওপর স্বামী পুরোপুরি বিরক্ত হয়ে উঠল। এক গান আর কত গাওয়া যায়! সে বরং একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে থাকে। দুজনের মধ্যে তেমন কথাবার্তা হয় না।
*** *** ***
এক সন্ধ্যায় স্বামীকে একটা মিটিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য যেতে হল। সেখানে রাতের খাবারের আয়োজনও ছিল। বিয়ের পর এই প্রথম সে দীর্ঘ সময়ের জন্য রাতে বাড়ির বাইরে থাকতে যাচ্ছে। স্ত্রীর বেশ মন খারাপ। স্বামী তাকে অনেক করে বোঝালো। বলল, সন্ধ্যার সময়টা যেন সে আশেপাশের কোন বান্ধবীর সাথে গল্প করে কাটায়, আর রাতে যেন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ, সব কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে হয়ত গভীর রাত হয়ে যাবে।
সন্ধ্যায় স্ত্রীর এক বান্ধবী এল। রাত্রি নয়টা পর্যন্ত তারা নানা গল্পগুজব করল। সময় যেন কাটতেই চায় না। বান্ধবী এক সময় চলে গেল। সময় এবার আরও শভুকগতিতে চলছে। কিন্তু স্ত্রীও প্রতিজ্ঞা করেছে, স্বামী না ফেরা পর্যন্ত ঘুমুতে যাবে না। ড্রইংরুমে সোফার ওপর এককোণায় বসে রইল। শরীরে ক্লান্তি এলেও মনের অস্থিরতার কারণে ঘুম আসছে না। অতএব, ওভাবেই বসে থাকতে হল। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ বসে থাকা যায়? সময়তো কাটছেই না! কী করা যায়? কাজের লোকের ঘরে উঁকি দিয়ে। দেখল–অঘোরে ঘুমুচ্ছে। পুরনো ঘড়িটা টিক-টক শব্দ করছে। কী করা যায়? সুইসুতো নিয়ে বসল কিছুক্ষণ। তাতেও মন বসাতে পারল না। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো মাত্র দশটা বাজে। নাহ্! আরতো ভালো লাগছে না। এবার শুরু হল ঘরময় অস্থির পায়চারি। আসবাবপত্র টানাটানি করে। এপাশ-ওপাশ করল। এতসব করেও যখন কিছুতেই সময় যাচ্ছে না, স্ত্রী। তখন রীতিমত অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। আচ্ছা! বিয়ের মানে তাহলে এই? একটা মেয়েকে তার পরিবার-পরিজন থেকে দূরে সরিয়ে এনে তিন রুমের একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হবে, আর মেয়েটি স্বামী না-ফেরা পর্যন্ত ঘুম ঘুম চোখে অপেক্ষা করবে, তাই না? উহ! অসহ্য!
কিন্তু এটাতো ভুলে গেলে চলবে না যে, স্বামী তাকে ভালোবাসে, যথেষ্ট ভালোবাসে। সে তো অযথা বাইরে গিয়ে ঘোরাঘুরি করছে না; গেছে। অফিসের কাজে। এসব নিয়ে স্বামীর ওপর রাগ করাটা কি নিছক বোকামি নয়? হুম! কিন্তু স্বামী কি সত্যিই এখনো তাকে ভালোবাসে? এইতো দু’একদিন আগেই স্ত্রী যখন তাকে সুতার কাঠিমটা ধরে থাকতে বলল কই স্বামীতে রাজি হল না। অথচ বিয়ের আগে সুতার কাঠিম ধরে রাখাটা তার প্রিয় কাজ ছিল! আরও আছে, গতকাল লাঞ্চের আগে স্বামীর সাথে একবার দেখা করতে যাওয়ায় স্বামী ভুরু কুঁচকে ছিল, না? হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেছে সে! তবুও, সব কিছু না-হয় ছাড়া গেল, কিন্তু এই যে আজ সে মিটিংয়ে গেল, মিটিংয়ের পর রাতে সেখানে খাওয়ার দরকারটা কী?
স্ত্রীর চিন্তা-ভাবনা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছাল রাত্রি তখন সাড়ে দশটা। হঠাৎ করেই তার মনে হল–আচ্ছা, এমন চিন্তাতো আগে কখনো করিনি! সাথে সাথে আবার মন খারাপ হয়ে গেল। এবার আগের চেয়ে বেশি খারাপ হল। একে-একে নানা অসংগতি চোখে ধরা পড়তে লাগল: আরে! স্বামীকে আর আগের মত মধুরভাবে কথা বলে না, আগের মত গান গায় না, পিয়ানো বাজায় না। সর্বোপরি, স্বামী তার কাছে মিছে কথাও বলছে আজকাল। এইতো সেদিনই বলল, বিকালে না-ঘুমালে নাকি তার চলেই না; অথচ, কয়েকদিন ধরে সব সময়ই সে একটা ফ্রেঞ্চ নভেল পড়ছে; এমনকি বিকেলেও! ওফ! স্বামী তাকে মিথ্যা বলেছে!
এতসব চিন্তা করতে করতে রাত সাড়ে এগারোটা বাজল। চারদিকের সুনসান নীরবতা এখন গায়ে কাঁটা হয়ে ফুটছে। কেমন যেন দমবন্ধ লাগছে। স্ত্রী উঠে গিয়ে জানালা খুলে রাস্তায় তাকালো। দুটো লোক দুটো মেয়ের সাথে দর কষাকষি করছে। হুম! এটাই তাহলে পুরুষের আসল চরিত্র! আচ্ছা, তার স্বামী যদি কখনো এমন করে? ভাবতেই গা শিউরে উঠল। স্বামী এমন করলে সে নিশ্চিত আত্নঘাতি হবে! ঝট করে জানালা বন্ধ করে দিয়ে সোফার ওপর বসে পড়লো স্ত্রী। মনে পড়ল, স্বামী একবার তাকে বলেছিল: “যে যেমন ভাবে, সে তেমনই দেখে।” সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু যেন পরিবর্তিত মনে হল। চারপাশের সবকিছু কেমন নতুন, ঝা চকচকে দেখাচ্ছে! বিছানার ওপর সবুজ চাদরটাকে মনে হচ্ছে যেন সবুজে ছাওয়া কোন নির্মল মাঠ, আর তার ওপর রাখা বালিশ দুটো যেন ঘাসের ওপর শুয়ে থাকা ছোট্ট দুটো আদুরে বেড়ালছানা! ঘরের সব আসবাবের রোশনাই যেন দ্বিগুন হয়ে গেছে, দেয়ালে ঝোলানো আয়নাটার ওপর যে ছোপ-ছোপ দাগ ছিল সেগুলোও আজ উধাও! চিরুনি, পাউডার বক্স আর টুথব্রাশের গোড়ায় লাগানো রূপার প্রলেপ যেন আজ সোনার মত ঝকঝক করছে! এমনকি ঘরে পড়ার জুতো জোড়াও এমন নতুন আর চমৎকার লাগছে যে, ভাবাই যাচ্ছে না ওগুলো পায়ে পরার জিনিস! ওহ্! চারপাশে সবকিছু কত সুন্দর, কত নতুন, কিন্তু… কিন্তু প্রাণের ছোঁয়াটা যেন একটু কম। স্বামীর সবগুলো গান তার জানা, সব কথা, এমনকি সব চিন্তাও তার পরিচিত। খেতে বসার আগে স্বামী কী বলবে, সন্ধ্যাবেলায় ঘুরে বেড়ানোর সময় কী বলবে, সব তার বোঝা হয়ে গেছে। একই কথা, একই সবকিছু দেখতে দেখতে সে ক্লান্ত। আচ্ছা, কখনো কি সে ঐ লোকটির প্রেমে পড়েছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই পড়েছিল। তাহলে কি এই কথাগুলো, এই আচরণগুলোরই প্রেমে পড়েছিল? একটা মেয়ে হিসেবে সে যে স্বপ্নগুলো দেখেছিল সেগুলো মনে করার চেষ্টা করলো। হ্যাঁ, তার স্বপ্নগুলোও মোটামুটি এমনই ছিল। তাহলে কি মৃত্যু পর্যন্ত এই বৃত্তাকার পথেই জীবন চলতে থাকবে? হয়তো তাই। কিন্তু… কিন্তু… ইয়ে,… মানে,… তাদের বাচ্চা-কাচ্চা তো হবে এক সময়, তাই না? স্ত্রীর মুখটা জ্বলজ্বল করে উঠল। যদিও এখনও পর্যন্ত এমন কোন সম্ভাবনা দেখা যায়নি, তবু হবেতো এক সময়। তখন তাকে আর এমন একাকী সময় কাটাতে হবে না। স্বামী তখন যখন খুশি বাইরে যাক, যখন খুশি ফিরুক, তাতে কিছু যায়-আসে না; তার নিজের তো কথা বলার, সময় কাটানোর একজন থাকবেই। হয়তো মাতৃত্বই তাকে সুখী করতে পারবে। একজন পুরুষের বৈধ প্রেমিকা হয়ে থাকার চেয়ে মাতৃত্বের ব্যাপারটা অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ। ঐ সময়টা স্বামী তাকে ভালো না-বেসে পারবেই না। অথচ, এখন সে আর আগের মত ভালোবাসে না!
এসব চিন্তা করতে করতে স্ত্রীর চোখ ছলছল করে উঠল, ঝুরঝুরিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল।
স্বামী বাড়ি ফিরল রাত একটায়। এতক্ষণ কান্নাকাটি করে স্ত্রী এখন অনেকটা শান্ত। কিন্তু তাকে এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে দেখে স্বামী বেশ রেগে গেল। তার প্রথম কথাটাই হল এমন–“এত রাত হয়েছে তবু ঘুমাতে যাওনি কেন?”
–দেখতেইতো পাচ্ছ, তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অপেক্ষা করা মানুষ ঘুমায় কীভাবে?
–বাহ! চমৎকার যুক্তি, তো আমি কি তাহলে বাইরেও যেতে পারবো?
এ কথা জিজ্ঞেস করেই স্ত্রীর দিকে ভালো করে তাকালো স্বামী–“তুমি কি এতক্ষণ কান্না করছিলে?”
“হুম! করবো না কেন? তুমিতো আমাকে আর আগের মত ভালোবাসো না।” স্ত্রীর গলায় স্পষ্ট অভিমান।
–মানে কী? আমাকে অফিসের কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল বলেই কি তোমার মনে হল তোমাকে আর আগের মত ভালোবাসি না?
“রাতে বাইরে খাওয়াটা অফিসের কাজ হতে পারে না” ঠোঁট উল্টে স্ত্রীর প্রতিবাদ।
–হায় ঈশ্বর! তাহলে কি আমি বাইরেই যাবো না? উহ! মেয়েরা কেন। যে এত অনধিকারচর্চা করে!
–অনধিকারচর্চা? তোমার প্রতি আমার অনুভূতিকে অনধিকারচর্চা মনে হল তোমার? আমার আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। গতকালও তোমার অফিসে গিয়ে দেখা করার সময় এমন সন্দেহ হচ্ছিল। আর কখনোই তোমার সাথে দেখা করতে যাবো না।
স্বামী এবারে একটু হকচকিয়ে গেল–“ভুল বুঝোনা, সোনা! আমিতো আমার প্রধান…
উঁহু হু হু হু! স্ত্রী হাত-পা ছুঁড়ে কান্না জুড়ে দিল।
স্বামী বেচারা কী করবে ভেবে না-পেয়ে হৈচৈ করে কাজের লোককে ডেকে গরম পানির বোতল নিয়ে আসতে বলল। অথচ, আনার পর ধমক দিয়ে রুম থেকে বের করে দিল। তারপর, বোতল হাতে করেই হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে স্ত্রীর কান্না দেখতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর নিজেও অশ্রু বিসর্জন শুরু করল। গভীর, তিক্ত-বেদনাজাত অশ্রু। নিজের আচরণ, হৃদয়ের কঠিনতা, নানারকম শয়তানি, আর সর্বোপরি ভালোবাসার মোহময়তার কথা চিন্তা করে অশ্রু বিসর্জন করল সে। কিন্তু সূক্ষ বিচারে তার ভালোবাসাকে হয়তো ঠিক মোহ বলা যাবে না; কারণ সে তো সত্যিই স্ত্রীকে ভালবাসে, তাই না? হু! তা অবশ্য ঠিক। ওদিকে আবার স্বামী যখন হাঁটু মুড়ে বসে গোমড়ামুখো স্ত্রীর চোখের ওপর চুম্বন করছিল তখন স্ত্রীও তো বলছিল সে স্বামীকে ভালোবাসে, তাহলে? তাহলে কিছু না, তারা নিশ্চয়ই একে অপরকে ভালোবাসে। এতক্ষণ যেসব হচ্ছিল সেগুলো নিতান্তই কিছু কালো মেঘ। সে মেঘ এখন কেটে গেছে। আসলে, একাকী থাকার কারণেই এসব আজেবাজে চিন্তার উদ্রেক হয়। অতএব, স্ত্রী মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, সে আর কখনোই একাকী থাকবে না। দুর্যোগের ঘনঘটা কাটিয়ে তারা একে অপরের বাহুলগ্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। স্ত্রীর গালে মিষ্টি হাসির টোল দেখা গেল।
পরদিন স্ত্রী আর স্বামীর অফিসে দেখা করতে গেল না। স্বামী কিন্তু দুপুরে খেতে এসে এ নিয়ে একটা কথাও বলল না। তবে, অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি কথা বলল। কথা বলার সময় স্ত্রীর দিকে খুব একটা মনোযোগ ছিল না তার, বরং কিছুক্ষণ পর মনে হল যেন সে একা-একাই কথা বলছে। সন্ধ্যার সময় ‘যসতালম’ প্রসাদের জীবন যাপনের লম্বা বর্ণনা দিয়ে স্ত্রীকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করল স্বামী। তরুণীরা ব্যারনের সঙ্গে কীভাবে কথা বলে তা অভিনয় করে দেখালো, কাউন্টস এর ঘোড়াগুলোর নাম একে-একে বলে গেলো। কিন্তু এসবের কিছুতেই স্ত্রীকে বিশেষ উৎসাহিত মনে হলো না।
পরের দিন সন্ধ্যায় স্ত্রীকে নিজের গবেষণা প্রবন্ধের ব্যাপারে বলল স্বামী। এরপর থেকে ধীরে ধীরে সন্ধ্যায় তাদের গল্পের সময়টা খুব গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে কথা বলার সময়ে পরিণত হয়ে গেল।
*** *** ***
একদিন বিকেলে স্বামী ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল। স্ত্রী এতক্ষণ ড্রইংরুমে বসে অপেক্ষা করছিল, আর উল দিয়ে কাপড় বুনছিল। হঠাৎ, উলের বলটা হাত থেকে পড়ে গেল। স্বামী সে সময় সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। উলের সুতা ছড়িয়ে তার পায়ে জড়িয়ে গেল। ভীষণ রেগে গিয়ে স্ত্রীর হাত থেকে উলে বোনা-কাপড় টেনে নিয়ে সবকিছুসমেত উলের বলটাকে লাথি দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। এমন নির্দয় ব্যবহারে স্ত্রী চিৎকার করে উঠল। স্বামীর রাগ যেন পড়ছেই না। গলা চড়িয়ে বলল, এসব জঞ্জাল নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় তার নেই। স্ত্রীকে উপদেশ দিল লাভজনক কোন কাজ করতে। পেশাজীবনে উন্নতি করতে চাইলে নিজের গবেষণা-প্রবন্ধটা যেকোন মূল্যে এবার সম্পূর্ণ করতেই হবে। সেক্ষেত্রে, স্ত্রীর উচিত হবে এসব জঙ্গল নিয়ে বসে না-থেকে কীভাবে সংসারের খরচ কমানো যায় সে চিন্তা করা।
বোঝা যাচ্ছে, পানি বেশ দূর অব্দি গড়িয়েছে।
পরদিন জলভরা চোখে স্বামীর জন্য মোজা বানাচ্ছিল স্ত্রী। স্বামী বলে বসল, “ওগুলো আরও কমদামে রেডিমেড কিনতে পাওয়া যায়। স্ত্রীর চোখে এবার জলের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল। সে করবেটা কী তাহলে? কাজের মেয়েটাতো বলতে গেলে বাড়ির সব কাজই করে দেয়। রান্নাঘরে গিয়ে ওর সাথে হাত লাগানোর মত যথেষ্ট কাজ রান্নাঘরে নেই। তবুও, সে সবসময় নিজের গরজেই সব ঘরদোর ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে। তাহলে, তার কাছে স্বামী চায়টা কী? সে কি চায় কাজের মেয়েটাকে বিদায়। করে দেয়া হোক?
না-না তা নয়।
তাহলে সে কী চায়?
আসলে সে যে কী চায়, তা নিজেও ভালো করে জানে না। তবে, সে নিশ্চিত, কোথাও একটা কিছু গন্ডগোল হচ্ছে। না-হলে সংসার-খরচ এত বেশি হবার কথা না। বর্তমানে যেভাবে চলছে সেভাবে চলা তাদের পক্ষে। খুব বেশিদিন সম্ভব হবে না। আর, তাছাড়া এতসব চিন্তায় নিজের গবেষণা প্রবন্ধের জন্যও সে তেমন একটা সময় দিতে পারছে না। এইসব চিন্তা করতে করতেই কিছুদিন যাবৎ মাথাটা একটু গরম হয়ে আছে।
যাহোক, স্বামীর স্বীকারোক্তির পর আবারও চোখের জল আর চুম্বন পরবর্তী শান্তি স্থাপিত হল। তবে, এরপর থেকে স্বামী ঘরের বাইরে অনেক বেশি সময় দিতে থাকল। সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন সন্ধ্যার অনেক পর পর্যন্ত বাইরে থাকে। কারণ হিসেবে ঐ একটাকেই দাঁড় করানো হয় প্রতিবার ‘অফিসের কাজ। স্বামী অবশ্য ব্যাপারটাকে ইতিবাচকভাবেই দেখে–পুরুষ মানুষের নিজের ঠাঁট বজায় রেখে চলা উচিত; ঘরে বেশি থাকলে নিজের দাম থাকে না, সবাই তখন সস্তা মনে করে এক সময় অবজ্ঞা করতে শুরু করে।
এভাবেই একটি বছর পার হল। তখনও পর্যন্ত তাদের সন্তান হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। স্বামীর আজকাল একটা কথা প্রায়ই মনে হয়: আগে যে বিভিন্ন মেয়ের সাথে পরিচয় ছিল এখন স্ত্রীর সাথে সম্পর্কটা অনেকটা সেরকমই হয়ে গেছে। তবে, পার্থক্য শুধু একটাই–যেটাকে নিয়ে সংসার করছে সেটা নিতান্ত নিবোধ, আর বেশি খরুচে।
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখন বলতে গেলে কোন কথাই হয় না। যতটুকু হয়। সেটা নিতান্তই প্রয়োজনীয় সাংসারিক কথাবার্তা। স্বামীর মনে হয়, “এর। মাথায় বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। এর সঙ্গে কথা বললে মনে হয়, যেন নিজের সাথেই কথা বলছি!” স্ত্রীর চোখের সৌন্দর্য, যেটা নিয়ে একসময় খুব উচ্ছ্বাস। ছিল, সেই সৌন্দর্যেরও সে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে, “ওটা আসলে মনের ভুল। ওর চোখের তারাগুলো একটু বড় বলেই ও রকম মনে হয়; আদতে, ওর চোখে কোন গভীরতাই নেই, যেমন নেই বুদ্ধিতেও।”
স্বামী একসময় প্রকাশ্যেই স্ত্রীর প্রতি তার এমন অনুভূতির কথা বলতে শুরু করল। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কথাগুলো এমনভাবে বলত যেন সেটা বহু আগেই ক্ষয়ে গিয়েছে। অবশ্য, যখনই এমন কথা বলত তখনই সে হৃদয়ে একরকম যন্ত্রণা অনুভব করত। একটা অস্বস্তিকর, নির্মম, অনুশোচনাহীন-যন্ত্রণা; যে যন্ত্রণার কোন নাম নেই।
তবে, এসব নিয়ে সে বেশ গভীরভাবে চিন্তা করেছে। একদিন সব কিছুই শেষ হয়ে যায়, এই হলো চিন্তা-পরবর্তী উপলব্ধি। তথাপি, সে আরও চিন্তা করতে থাকলো। সবকিছুই যদি একসময় রংহীন হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর প্রিয় গানগুলোর ব্যাপারেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? “ঐ একই গান কাউকে যখন বছরে তিনশ পয়ষট্টি দিন শুনতে হয়, তখন তা পুরনো হতে বাধ্য। কিন্তু তাহলে কি এ কথাও সত্য যে, আমাদের ভালোবাসাও মারা গেছে?” স্ত্রীতো সে রকমই বলে। “না-না-না কিছুতেই না… অবশ্য…, হতেও পারে। আমাদের বিয়েটাতো এখন শুধু একটা বিশ্রী চুক্তি হয়েই আছে। আমাদেরতো কোন সন্তানই নেই।”
এ রকম নানা সাত-পাঁচ ভেবে, স্বামী একদিন এক বিবাহিত বন্ধুর সাথে এসব নিয়ে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল। হাজার হলেও তারা একই গোত্রভুক্ত!
–বিয়ে করেছ কতদিন হল?
–ছ’ বছর।
–আচ্ছা! এই দীর্ঘ সময়ে বৈবাহিক বিষয়ে কখনো বিরক্ত হওনি?
–হতাম, প্রথম দিকে হতাম। ছেলেপুলে হবার পর সেসব কেটে গেছে।
–তাই নাকি? তাহলে তো ছেলেপুলে না-থাকায় আমরা বেশ দুর্ভাগা মানতে হবে।
–উঁহু! এ তোমাদের দোষ নয় দোস্ত! বউকে বলো ডাক্তার দেখাতে।
বন্ধুর সঙ্গে আলাপ শেষে বাড়ি ফিরে বহুদিন পর স্ত্রীর সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলল স্বামী। স্ত্রীকে সবকিছু বুঝিয়ে বলার পর সে ডাক্তার দেখাতে রাজি হল।
দু’সপ্তাহ পর বাড়িতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা গেল।
পুরো বাড়িতে যেন কী এক চঞ্চলতা ভর করেছে। ড্রইংরুমের টেবিলের ওপরে, এখানে-ওখানে, বাচ্চাদের পোশাক আলুথালু হয়ে পড়ে থাকে। হঠাৎ করে কেউ ঘরে ঢুকলে সেগুলো গোছানোর জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পরে যখন দেখা যায়, মানুষটা অন্য কেউ নয়, তার স্বামী, তখনই সেগুলো আবারও যথাস্থানে ফিরে আসে! শুরু হয় নানা জল্পনা-কল্পনা। বাচ্চার জন্য নাম ঠিক করতে হবে। ওরা মোটামুটি নিশ্চিত, ছেলে সন্তানই হবে। সুতরাং, ছেলেদের নামের তালিকা তৈরি করা হল। অবশ্য, আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এর মধ্যে করতে হবে–স্ত্রীকে নিয়মিত ডাক্তার দেখাতে হবে, মেডিকেল বই বানাতে হবে, বাচ্চার খেলনা-দোলনা কিনতে হবে, আরও কত কি…
*** *** ***
অবশেষে সন্তানের আগমন ঘটল। সত্যিই একটা ছেলে হল। স্বামী যখন দেখল তার ছোট্ট বানরছানাটি(!) স্ত্রীর বুকের দুধ পান করছে তখন একরকম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্ত্রীর মধ্যে মাতৃত্ব আবিষ্কার করল সে। যখন দেখল, স্ত্রীর বড় বড় চোখ দুটি পরম মমতায় সন্তানের দিকে তাকিয়ে আছে তখন মনে হল, স্ত্রী যেন সন্তানের মুখে চেয়ে ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছে। আর ঠিক তখনই সে নতুন করে অনুভব করল, আসলেই স্ত্রীর চোখে গভীরতা আছে। সে গভীরতা এতটাই বেশি যে স্বামীর সমস্ত ধর্মকাহিনি আর নাটক দিয়েও তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। স্বামীর সমস্ত পুরনোভালাবাসা, প্রিয় পুরনো ভালবাসা, নতুন স্ফুলিঙ্গের মধ্য দিয়ে জ্বলে উঠল যেন। নতুন সে স্কুলিঙ্গে নতুনতর একটা কিছু যোগ হয়েছে, যার খানিকটা সে অনুভব করেছে মাত্র, পুরোপুরি এখনও বুঝে উঠতে পারেনি!
“ইস! স্ত্রী যখন এটা-সেটা নিয়ে ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করে তখন ওকে কী চমৎকার দেখায়! আর, বাচ্চার যেকোন সমস্যা কী অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সাথেই না সমাধান করে!” সত্যি, তার স্ত্রী বুদ্ধিমতী বলতে হবে!
ওদিকে স্বামীর মধ্যেও কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে। ইদানিং সে নিজেকে একজন দায়িত্ববান পুরুষ বলে ভাবে। ব্যারনের ঘোড়া আর কাউন্টসদের ক্রিকেট খেলার গল্প না-করে বরং সারাক্ষণ ছেলের গল্পই করে; সম্ভবত একটু বেশিই করে! মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় যখন বাইরে যেতে হয়, সেই পুরো সময়টা মন পড়ে থাকে ঘরের মধ্যে। অবশ্য, এই কারণে নয় যে স্ত্রী বসে তার জন্য অপেক্ষা করছে, বরং, এই ভেবে যে, স্ত্রী এখন আর একা বসে অপেক্ষা করে না! বাড়িতে ফিরে দেখে মা-ছেলে দুজনেই পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাচ্চাটাকে মাঝে মাঝে একটু ঈর্ষাই হয়। নিজে বাইরে থাকার সময় কেউ একজন বাড়িতে একা বসে অধীরভাবে অপেক্ষা করছে এই চিন্তাটার মধ্যে এক ধরনের অদ্ভুত আনন্দ আছে, যে আনন্দটা থেকে সে এখন বঞ্চিত। তার কারণতো ওই বাচ্চাটাই।
যা হোক, স্বামী এখন চাইলে বিকেলে ঘুমাতে পারে। কারণ, তার ঘুমানো বা না-ঘুমানোতে কারো কিছু যায় আসে না। সে অফিসের কাজে বাইরে যাওয়ামাত্র পিয়ানো বের করে আনা হয়। সেই পুরনো ‘বুনো গোলাপ’ গানটা বাজানো হয়। সে গানে আবার নতুনত্ব এসেছে; কারণ, ছোট্ট হারল্ডতো এ গান আগে শোনেনি। তাছাড়া, অনেক দিন বাদে শোনার কারণে হারল্ডের মায়ের কাছেও গানটা এখন নতুন বলে মনে হয়।
স্ত্রীর এখন উল দিয়ে জামাকাপড় বোনার মত যথেষ্ট সময় নেই। ঘরে। এখন এমনিতেই রেডিমেড কেনা অসংখ্য ছোট-ছোট জামাকাপড় রয়েছে। ওদিকে, স্বামীও তার গবেষণাপ্রবন্ধে অতটা সময় দেয় না–“থাক, ওটা না হয় হারল্ড বড় হয়ে করবে।” প্রায় সন্ধ্যাতেই স্বামী-স্ত্রীকে পাশাপাশি বসে গল্প করতে দেখা যায়। তবে, এটাকে এখন আর গল্প না বলে আলোচনা। বলাটাই ভালো। কারণ, স্ত্রীও এখন কথা বলায় অংশগ্রহণ করে। সে জানে, কোন্ বিষয় নিয়ে কীভাবে কথা বলতে হবে। আর, এটাও স্বীকার করে, আগে সে নিতান্ত বোকাসোকা একটা মেয়ে ছিল–ধর্মকাহিনি কিংবা নাটক সম্পর্কে কোন জ্ঞান না-থাকায় চুপচাপ বসে থাকত। স্বামীকে বহুবার বলারও চেষ্টা করেছে, কিন্তু স্বামী সে কথায় কান দেয়নি। স্বামী অবশ্য এখনও কান দেয় না!
স্বামী-স্ত্রী এখন একসাথে তাদের প্রিয় গানটা গায়। ফোকলা দাঁতের হাসি দিয়ে ছোট্ট হারল্ডও তাতে অংশ নেয়। সে হাসি যেন নতুন ছন্দ যোগায়। ছন্দের তালে ওরা গা এলিয়ে দেয়, সেই তালেই দোলা দেয় দোলনাতে। পুরনো গানটা যেন ভীষণ জীবন্ত হয়ে উড়ে বেড়ায় ঘরময়…
দেনা-পাওনা
মিস্টার ব্ল্যাকউড ব্রুকলিনের কাছে একটা জাহাজ-জেটিতে কাজ করেন। সম্প্রতি মিস ড্যাঙ্কওয়ার্ড নামের এক ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করে মোটা অঙ্কের যৌতুক পেয়েছেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, বাসা-বাড়িতে থাকলে কাজ করতে গিয়ে স্ত্রী হয়তো মন ছোট করে থাকতে পারেন; কিংবা, নিজেকে হয়তো পরাধীন বলে ভাবতে পারেন! তাই ঝামেলা এড়াতে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি একটা হোটেলে উঠলেন। এখন থেকে এখানেই থাকা হবে!
হোটেলে সারাদিনে স্ত্রীর করার মত তেমন কোন কাজ নেই। সময় কাটে বিলিয়ার্ড খেলে, আর পিয়ানো বাজিয়ে। রাতের অর্ধেকটা কাটে নারী অধিকার নিয়ে নানা বিপ্লবী আলোচনা করে, আর হুইস্কি খেয়ে।
স্বামীর বেতন পাঁচ হাজার ডলার। এর পুরোটাই তিনি স্ত্রীর হাতে তুলে দেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেটা স্ত্রীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এর বাইরেও পোশাক আশাকের খরচা বাবদ তাকে আরও পাঁচশ ডলার দেয়া হয়, যেটা দিয়ে সে যা খুশি তাই করতে পারে।
কিছুদিন পর তাদের সন্তান হল। সন্তানের দেখাশোনার জন্য একশো ডলার দিয়ে একজন নার্স রাখা হল। এই নার্সই মায়ের মত করে বাচ্চাটির যত্নআত্তি করে। সময়ের সাথে সাথে তাদের আরও দুটি সন্তান হল। সন্তানেরা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। কিন্তু এসব নিয়ে ব্ল্যাকউডপত্নীর কোন মাথাব্যথা নেই। তার বরং দিন-দিন আরও বেশি একঘেয়ে লাগে।
একদিন সকালে কিঞ্চিৎ মাতাল অবস্থায় স্ত্রীকে নাস্তার টেবিলে দেখা গেল। স্বামী মোটামুটি দুঃসাহসিক পর্যায়ের(!) একটা কাজ করলেন, স্ত্রীকে বলে বসলেন–“তোমাকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে।” এ-কথা শুনে স্ত্রীরতো রীতিমত মৃগীরোগীর মত অবস্থা! খাবার টেবিল ছেড়ে তিনি খাটে গিয়ে পড়লেন। খবর পেয়ে হোটেলের অন্যান্য রুমের মহিলারা ফুল নিয়ে তাকে দেখতে এলেন। অত্যাচারী স্বামীর প্রতি নানা বিষোদ্গার করলেন। এরা চলে গেলে ধীরে-সুস্থে এলেন স্বামী। যথাসম্ভব মমতাভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি এত মদ্যপান কেন কর, বলতো? কোন কারণে কী তুমি নিজেকে অসুখী মনে কর?”
“আমি কীভাবে নিজেকে সুখী মনে করি, বলো? আমার পুরো জীবনটাই যে অপচয় হল!” কান্নাভেজানো কণ্ঠে জবাব দিলেন স্ত্রী।
“এসব তুমি কী বলছ?” স্বামী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। “অপচয় বলতে তুমি কী বোঝ? তোমার তিন-তিনটা ছেলেমেয়ে আছে। চাইলেই ওদের দেখাশোনা করে, শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে তুমি সময় পার করতে পার।”
–নিজের ছেলেমেয়েদের কোন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো আমার পছন্দ না।
–তাহলে তুমি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতে পার। সেক্ষেত্রে, তোমার জীবনের একটা মহান লক্ষ্য থাকবে, তোমার জন্য অন্যেরা উপকৃত হবে, আর সর্বোপরি পুরো সমাজ তোমাকে সম্মান দেবে। অন্তত, জাহাজ-জেটির কর্মচারীর চেয়ে বেশি সম্মানতো বটেই!
–হুম, সবই ঠিক আছে। কিন্তু ইস! আমি যদি স্বাধীন হতাম!
স্বামী এবারে মরিয়া হয়ে উঠলেন, “তুমি অবশ্যই স্বাধীন; অন্তত আমার চেয়ে বেশি স্বাধীন। ভেবে দেখ, সবসময় তুমিই সিদ্ধান্ত নাও আমার উপার্জন কীভাবে, কোনপথে খরচ হবে। আমি বরং তোমার কর্তৃত্বে থাকি। নিজের ইচ্ছামত খরচের জন্য তুমি মাসে পাঁচশ ডলার হাতখরচ পাও; অথচ আমাকে দেখ, আমার কিন্তু কোন হাত-খরচ নেই। আমার কোন খরচাপাতি লাগলে, এমনকি সিগারেট কেনার টাকাও তোমার থেকে চেয়ে নিতে হয়। এত কিছুর পরও তোমার মনে হয় না, তুমি আমার চেয়ে স্বাধীন?”
স্ত্রী কোন জবাব দিলেন না। মনে হল, শেষের প্রশ্নটা তিনি শুনতেই পাননি! তবে এ আলোচনার ফলাফল বেশ ব্যাপক হল। সিদ্ধান্ত হল, হোটেল ছেড়ে এবার তারা বাসাবাড়িতে উঠবে। বাড়ির পরিবেশে হয়ত মন চনমনে থাকবে। তাছাড়া বাড়ির খরচাপাতির খুঁটিনাটি হিসাব রাখার ব্যাপারেও মনস্থির করা হল–এতে অন্তত করার মত কিছু কাজ পাওয়া যাবে।
*** *** ***
কিছুদিন পরের ঘটনা। ব্ল্যাকউডপত্নী তার এক বান্ধবীকে চিঠি লিখলেন
বন্ধু,
আমি অসুস্থ। ক্লান্ত-শ্রান্ত আমি যেন দিন-দিন মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছি। জানি, এমন কষ্টের মধ্য দিয়েই আমাকে যেতে হবে। কারণ যে নারীর জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই, তার জন্য জগতে কোন সান্ত্বনা নেই, তার মত দুঃখীও কেউ নেই। কিন্তু আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। জগৎকে দেখিয়ে দেব, স্বামীর টাকায় খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মত মেয়ে আমি নই। আর একারণেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি কাজ করতে শুরু করব; মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে যাবো আমি….
অতঃপর, ব্ল্যাকউডপত্নীর কর্মময় জীবন শুরু হল। প্রথমদিন তিনি সকাল নয়টায় ঘুম থেকে উঠলেন। স্বামীর রুমটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করলেন। কাজের লোককে সরিয়ে দিয়ে নিজেই রান্নাবান্না করতে শুরু করে দিলেন। দুপুর একটার সময় ব্ল্যাকউড সাহেব যখন লাঞ্চ করতে বাড়ি এলেন, খাবারদাবার তখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। দোষটা অবশ্য কাজের লোকেরই হল! যাহোক, স্ত্রীর কালিঝুলিমাখা ক্লান্ত চেহারা দেখে স্বামী বেচারা খাবার নিয়ে কোন অভিযোগ করলেন না। চুপচাপ একখানা আধপোড়া কাটলেট খেয়ে আবার কাজে বের হয়ে গেলেন। যাবার সময় স্ত্রীকে বলে গেলেন “এত খাটাখাটনি করো না, সোনা! শরীর খারাপ করবে।”
সন্ধ্যাবেলায় ব্ল্যাকউডপত্নী এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন যে বাকি কাজ শেষ করা আর সম্ভব হল না। দশটার দিকে তিনি ঘুমুতে গেলেন।
পরদিন সকালবেলা ব্ল্যাকউড সাহেব স্ত্রীর রুমে গেলেন। বেশ অবাক হলেন তিনি স্ত্রীকে আজ অন্যদিনের চেয়ে একটু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে যেন! ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিজ্ঞেসই করে বসলেন, “রাতে নিশ্চয়ই ভালো ঘুম হয়েছে?”
“হঠাৎ এমন প্রশ্ন কেন?” স্ত্রীকে সন্দিগ্ধ দেখালো।
“কারণ, আজ তোমাকে অন্যদিনের চেয়ে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে” হাসতে হাসতে বললেন স্বামী।
“আমাকে সু……র দেখাচ্ছে?” থেমে থেমে শব্দটা উচ্চারণ করলেন স্ত্রী।
“হুম! একটু-আধটু কাজ করাটা বোধহয় তোমার জন্য ভালোই।” স্বামীর সপ্রশংস মন্তব্য।
তবে এর ফল কিন্তু হল উল্টো।
–“একটু-আধটু? একে তোমার একটু-আধটু কাজ মনে হয়েছে? তা কতটুকু হলে তোমার কাছে বেশি কাজ মনে হবে, শুনি?” স্ত্রীর চোখ-মুখ দিয়ে যেন ঝাঁজ বেরুচ্ছে।
স্বামী বেচারা ঘাবড়ে গেলেন–“দেখ, আমি কিন্তু সে রকম কিছু বলিনি। তোমাকে কষ্ট দেয়ার কোন ইচ্ছাই আমার নেই।”
“অবশ্যই আছে” আগের মতই রেগে আছেন স্ত্রী। “তুমি স্পষ্ট বোঝাতে চেয়েছ, গতকাল আমি যথেষ্ট কাজ করিনি! অথচ ভুলে গেছ, সবার আগে আমি তোমার রুমটাই পরিষ্কার করেছি। মানে, আমি বোধহয় কাজের লোক হলেই ভালো হত, না? সারাদিন কাজ করতাম, রান্না। করতাম, ঘর গোছাতাম। তাহলে নিশ্চয়ই তুমি খুশি হতে। তুমি অস্বীকার। করতে পার আমি তোমার দাসী নই?”
স্বামী এ অবস্থাকে আর দীর্ঘায়িত হতে দিলেন না। চুপচাপ রুম থেকে চলে এলেন। বাইরে যাবার সময় কাজের লোককে বেশ শাসিয়ে গেলেন “এখন থেকে সকাল সাতটায় উঠে আমার রুম পরিষ্কার করবি। ম্যাডামকে যেন আর তোর কাজ করতে না হয়।”
সন্ধ্যাবেলা ব্ল্যাকউড সাহেব বেশ খোশমেজাজে ঘরে ফিরলেন। স্ত্রী কিন্তু তখনো রেগে ছিলেন। আমাকে তোমার রুম পরিষ্কার করতে দেয়া হল না কেন?” থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করলেন।
–কারণ ‘তুমি আমার দাসী’, এই অভিযোগ আমি মানতে পারি না।–কেন মানতে পার না?
–আমি ওভাবে কখনো চিন্তাও করিনি। ওভাবে চিন্তা করতে আমার কষ্ট হয়।
–ও আচ্ছা, এই কথা! কিন্তু আমাকে দিয়ে রান্নাবান্না করাতে, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করাতে কষ্ট হয় না?”
স্বামী এ-প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, অন্যরুমে চলে গেলেন। পরদিন ট্রামে করে অফিসে যাবার পথে, পুরো সময়টা তিনি এইসব ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করলেন। সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরলেন, ততক্ষণে তাঁর বেশ গোছালো চিন্তাভাবনা হয়ে গেছে। এবার স্ত্রীকে নিয়ে বসলেন তিনি–“শোন ডার্লিং, বাড়িতে তোমার অবস্থান নিয়ে খুব গুছিয়ে একটা চিন্তা করেছি। তবে তার ফল কিন্তু তুমি যা বলেছিলে তার পুরোপুরি বিপরীত দাঁড়িয়েছে। কোনভাবেই আমার মনে হয়নি, তুমি এ বাড়ির কাজের লোক বা আমার দাসী। কিন্তু তবুও, তোমার যেহেতু মনে হয়েছে, আমরা একটা মধ্যবর্তী কোন উপায় বের করতে পারি। আমার মতে সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে, এখন থেকে তুমি নিজেকে বোর্ডিং হাউসের মালিক বলে মনে করবে, আর আমি বোর্ডার হিসেবে মাসে-মাসে তোমাকে ভাড়া দেব। অর্থাৎ, কী তুমিই থাকলে। আমি যে বোর্ডিংয়ে খাওয়াদাওয়া করছি, সেই বাবদ খরচও তোমার কাছেই দেব।”
স্ত্রী কেমন হকচকিয়ে গেলেন–“কী বলতে চাইছ?”
–বললামতো, খুব সহজ! আমরা এখন থেকে মালিক আর ভাড়াটিয়া হলাম। তবে ব্যাপারটা আমরা শুধু মনে মনেই রাখবো, আমাদের সম্পর্কে এর কোন প্রভাব পড়বে না।
–আচ্ছা বেশ! তা তুমি আমাকে কী পরিমাণ ভাড়া দেবে?
–সেই পরিমাণ, যে পরিমাণ দিলে আমাকে তোমার কাছে ঋণী থাকতে না হয়! আশা করি, এতে আমার নিজের অবস্থানেরও উন্নতি হবে। কারণ তখন আমার আর মনে হবে না, আমি কারও দয়ার ওপর বেঁচে আছি!
–দয়ার ওপর?
“নয়তো কী? তুমি আমাকে খেতে দিচ্ছ আধাসিদ্ধ খাবার; অথচ, বলে বেড়াচ্ছ–তুমি আমার চাকরানি, আমার জন্য কাজ করতে করতে তুমি মরে যাচ্ছ!” কথাগুলো বলার সময় স্বামীকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখালো।
“তুমি আসলে ঠিক কী বোঝাতে চাইছ, বলতো?”
–তেমন বিশেষ কিছু না। শুধু বলছি, বোর্ডার হিসেবে দিনে ত্রিশ ডলার দিলে চলবে তো? অন্য যেকোন বোর্ডিং হাউস কিন্তু বিশ ডলারেই রাজি হবে।
–চলবে, ত্রিশ ডলারেই চলবে।
“বেশ, তাহলে মাসে দাঁড়াচ্ছে প্রায় হাজার ডলার। আর আমি প্রথম মাসের টাকাটা অগ্রিম দিচ্ছি–এই নাও এক হাজার ডলার।” পকেট থেকে একটা হাজার ডলারের নোট আর কাগজ-কলম বের করলেন ব্ল্যাকউড সাহেব। স্ত্রীর হাতে নোটটা গুঁজে দিয়ে, সংসারের পুরো মাসের খরচ একটা বিল আকারে লিখলেন। বিলটা এরকম
ভাড়া–৫০০ ডলার
নার্সের বেতন–১০০ ডলার
রাধুনির বেতন–১৫০ ডলার
স্ত্রীর ভরণপোষণ–৫০০ ডলার
স্ত্রীর হাত-খরচ–৫০০ ডলার
নার্সের আনুষঙ্গিক খরচ–৩০০ ডলার
রাধুনির আনুষঙ্গিক খরচ–৩০০ ডলার
ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ–৭০০ ডলার
ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়–৫০০ ডলার
জ্বালানি, কাঠ, অন্যান্য–৫০০ ডলার
সর্বমোট–৪০৫০ ডলার
এবার স্ত্রীকে বললেন, “সংসার যেহেতু দুজনেরই, অতএব এই ৪০৫০ কে ২ দিয়ে ভাগ কর। কত হল? ২০২৫ ডলার। অর্থাৎ, আমাদের যার-যার ভাগে পড়ল ২০২৫ ডলার করে। তাহলে তোমাকে কিছুক্ষণ আগে যে ১০০০ ডলার দিলাম, সেটা তোমার ভাগের ২০২৫ ডলার থেকে কেটে রেখে, বাকি ১০২৫ ডলার আমাকে ফেরত দাও!”
স্ত্রী মনে হল সব গুলিয়ে ফেলেছেন। কোনমতে আমতা-আমতা করে বললেন, “ইয়ে মানে, তুমি কী চাচ্ছ যে, আমি এখন তোমাকে টাকা দেব?”
“অবশ্যই, যেহেতু আমরা সমান-সমান, অতএব ব্যাপারটাতো তা-ই দাঁড়াচ্ছে। সেক্ষেত্রে, তোমার আর সন্তানদের খরচের শুধু অর্ধেকটা আমার বহন করার কথা, তাই না? নিয়মতো তা-ই বলে।” খুব যত্ন করে গুছিয়ে কথাগুলো বললেন স্বামী। তাঁর কথা তখনো শেষ হয়নি, “নিয়ম ভঙ্গ করে পুরো খরচ আমি একাই দেব এমনটা নিশ্চয়ই তুমি আশা কর না? কারণ, সেক্ষেত্রে তো আমাকে ৪০৫০ ডলার ছাড়াও বোর্ডিং ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত ১০০০ ডলার তোমাকে দিতে হবে। কিন্তু আমি তো আমার ভাগের ২০২৫ ডলারের বাইরেও শুধু ভাড়া বাবদ ১০০০ ডলার তোমাকে দিচ্ছিই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ২০২৫ ডলারের বিনিময়ে আমি কী পাচ্ছি? পাচ্ছি, অতি উপাদেয়(!) খাবারদাবার। শুধু এই অতি-উপাদেয়(!) খাবারের জন্য নিশ্চয়ই আমাকে পুরো ৪০৫০ ডলার দিতে হবে না?
এতক্ষণ হাঁ করে সব শুনছিলেন স্ত্রী। তাঁকে যে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তা বুঝতেই পারেননি। স্বামী দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর কোনমতে শুধু বললেন, “বুঝতে পারছি না।”
“শুরুতে আমিও বুঝিনি। তবে এটুকু পরিষ্কার যে, আমার ভাগের টাকাটা দিয়ে দেবার পর আমি আর কোনভাবেই তোমার কাছে ঋণী থাকবো না। খুব ছোট্ট একটা ঘটনা খেয়াল কর–সবকিছুর মত কাজের লোকের খরচেও আমার ভাগ আছে, অথচ ওরা কিন্তু সারাদিন তোমার কাজই করে। তোমার তত্ত্ব মেনে নিয়ে, তুমি-আমি যদি সত্যিই সমান হই; কিংবা, যদি সত্যিই পুরুষ মানুষ সবকিছুতে বেশি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু এমন হবার কথা না। তোমার ঘরের কাজের প্রতি (সত্যিই যদি কিছু করে থাকো!) সম্মান দেখিয়েই বলছি তোমার তত্ত্ব অনুযায়ী, ঘরের কাজই যদি বেশি মূল্যবান হয়, তাহলে তোমার এটাও ভুলে যাওয়া উচিত হবে না, গৃহস্থালির খরচ বাবদ ৫০০ ডলারের বাইরেও হাত খরচ হিসেবে তুমি আরও ৫০০ ডলার পাচ্ছ; অথচ আমার কিন্তু হাত-খরচ বলতে কিছু নেই।”
এবার যেন স্ত্রীর চোয়াল ভেঙে পড়ল। অসহায়ভাবে বললেন, “আমি সত্যিই তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।”
স্বামীও হাল ছাড়ার পাত্র নয়। এবার অন্যভাবে শুরু করলেন–“ঠিক আছে, ‘বোর্ডিং হাউস তত্ত্ব বাদ দেয়া যাক। তার চেয়ে বরং, ডেবিট ক্রেডিট পদ্ধতিতে হিসাব করি চল।” এবার আরও গুছিয়ে, রীতিমত ব্যাংক হিসাবের আদলে একটা হিসাবপত্র দাঁড় করালেন ব্ল্যাকউড সাহেব।
বরাবর
মিসেস ব্ল্যাকউড
বিষয় : মিসেস ব্ল্যাকউডকে ঘর-গৃহস্থালির খরচ বাবদ দেয়া অর্থের হিসাব
বাড়ি ভাড়া এবং আনুষঙ্গিক–১০০০ ডলার তাঁর
কাপড়চোপড়–৫০০ ডলার
তাঁর হাত-খরচ (নগদ প্রদান)–৫০০ ডলার
বাচ্চাদের খরচ–১২০০ ডলার
কাজের লোকের (যারা শুধু তাঁর কাজই করে) খরচ–৮৫০ ডলার
সর্বমোট–৪০৫০ ডলার
যার অর্ধেক অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন—
জনাব ব্ল্যাকউড, জাহাজ-জেটির কর্মচারী
……………………..
স্বাক্ষর
স্ত্রীর পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না, “উফ! তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে বিলের হিসাব করছ, ছিঃ!”
–না না, শুধু স্ত্রীর খরচের হিসাবতো করছি না। স্ত্রীর কাছে নিজের পাওনার হিসাবও করছি।
ব্ল্যাকউডপত্নী এবারে বিলের কাগজগুলো খপ করে নিজের হাতে নিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কোমরে হাত দিয়ে স্বামীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন–“তাহলে কি তোমার সন্তানদের লেখাপড়ার খরচও আমাকে দিতে হবে?”
“তাই-ই তো দেয়া উচিত। কিন্তু ঠিক আছে যাও, সন্তানদের পড়ালেখার পুরো খরচটা না-হয় আমিই দেব; তোমাকে এক পয়সাও দিতে হবে না। তবে মনে রেখ, এটা কিন্তু সমতা হল না। যাহোক, সন্তানদের পড়ালেখা আর কাজের লোকের খরচের টাকাটা আমার ভাগে নিলাম; তারপরও, তোমার কাছে আমার আরও কিছু পাওনা থেকে যায়। সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে আরেকটা বিল তৈরি করে দেব?”
স্ত্রী আর কোন বিল চাইলেন না।
তিনি আর কখনোই কোন বিল চাননি।
পরিবর্তনের প্রচেষ্টায়
ব্যাপারটা তার মধ্যে বেশ ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। দীর্ঘদিন বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের গল্পের নায়িকার মনে হয়েছে–মেয়েদের আসলে দেখাশোনা করে বড় করা হয় শুধুমাত্র তাদের ভবিষ্যৎ স্বামীদের গৃহপরিচারিকা হবার জন্য! তাই, এ-জাতীয় পরিস্থিতি এড়াতে সে এখন থেকেই একটা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছে, যাতে যেকোন পরিস্থিতিতে নিজের পায়ে ভর করে থাকা যায়। ব্যবসাটি ছোট হলেও চমৎকার–কৃত্রিম ফুল বানিয়ে বিক্রি করা। এর যাবতীয় যোগাড়যন্ত্র সে নিজেই করে।
অন্যদিকে, আমাদের নায়কও একটা বিষয় নিয়ে বেশ হতাশ। সে লক্ষ করেছে, মেয়েরা অপেক্ষাই করে থাকে যেন স্বামীর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায়। এই-নিয়ে তার আক্ষেপেরও শেষ নেই। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এমন মেয়েকে বিয়ে করবে যে নিজে রোজগার করে, যে স্বাধীনচেতা, আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী। এমন কোন মেয়েকেই সে গ্রহণ করবে জীবনসঙ্গী হিসেবে, গৃহপরিচারিকা হিসেবে নয়। অতএব, দুজনের সাক্ষাৎ হওয়াটা বোধহয় ভাগ্যই ঠিক করে রেখেছিল।
এবারে চলুন বিস্তারিত জানা যাক–আমাদের নায়ক পেশায় একজন চিত্রকর, আর নায়িকার কথাতো আগেই বলেছি। এ বিপ্লবী চিন্তাভাবনা করার সময়টা তারা দুজনেই প্যারিসে থাকতো। অর্থাৎ, একই শহরনিবাসী। শীঘ্রই ভাগ্য তাদের সাক্ষাৎ ঘটালো, এবং পরিচয় থেকে পরিণয়ে গড়াতে খুব বেশি সময় লাগলো না। তবে, তাদের বিয়ে এবং বিয়ে-পরবর্তী জীবন বেশ ভিন্নরকম হল–তিন রুমের একটা ঘর ভাড়া নিয়ে মাঝের রুমটা ঠিক। করা হল স্টুডিও হিসেবে। ডানদিকে স্বামী, আর বামদিকে স্ত্রীর রুম। অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর এক-রুমে, এক-খাটে থাকার রীতিকে ঝেটিয়ে বিদায়। করা হল–“উহ! জগতে এমন জঘন্য রীতি বোধহয় আর দ্বিতীয়টি নেই! এই একসাথে থাকার রীতি থেকেই দুনিয়ার যত পাপাচার, যত দুষ্কর্মের শুরু!” স্বামী-স্ত্রী পৃথক রুমে থাকায় আরেকটা বিশ্রী ব্যাপারের অবসান
হলো–একই রুমে জামা-কাপড় পরা কিংবা খোলার সমস্যা আর রইল না। এসব ব্যাপারে দুজনেরই অভিন্ন মত–“স্বামী-স্ত্রীর পৃথক রুম থাকাই ভালো। যার-যার মত স্বাধীনভাবে থাকা যায়। বিশেষ দরকারে দেখা করার জন্য নিরপেক্ষ স্থান হিসেবে স্টুডিওতো আছেই!”
*** *** ***
বাড়িতে কোন কাজের লোক ছিল না। বেশিরভাগ কাজ দুজন মিলেমিশে করে ফেলত। সকাল-সন্ধ্যায় এক বুড়ি ঠিকা-ঝি এসে টুকিটাকি কাজগুলো করে দিয়ে যেত। সবমিলিয়ে বেশ ভালোই সময় কাটছিল ওদের।
নিন্দুকেরা বলে,”কিন্তু ছেলেপুলে হলে কী করবে, বাছাধন?”
–আহাম্মক! ছেলেপুলে কখনো হবেই না!
স্বামী-স্ত্রী এভাবেই দিন গুজরান করছিলো। স্বামী সকালবেলা বাজারে গিয়ে সদাইপাতি করে, ঘরে ফিরে কফি বানায়। স্ত্রী ঘরদোর গোছগাছ করে রাখে। তারপর বেলা হলে যে-যার কাজে লেগে পড়ে। কাজ করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে নিজেদের মধ্যে খানিক গল্পগুজব করে নেয়। কোনও আজেবাজে বিষয় নিয়ে তারা কখনোই গল্প করে না; বরং, বেশ উচ্চমার্গীয় আলাপ চলে তাদের মধ্যে, একে-অন্যকে নানা উপদেশ দেয়। মাঝে হয়তো কিঞ্চিৎ হাসি বিনিময়। দুপুরে স্বামী গিয়ে চুলা জ্বালায়, স্ত্রী শাকসবজি কাটে। যেদিন গরুর গোশত থাকে, সেদিন স্বামী রান্না করে, আর স্ত্রী মুদি দোকানে গিয়ে টুকিটাকি জিনিস কিনে আনে। ঘরে ফিরে স্ত্রী খাবার টেবিল গোছায়, স্বামী খাবার পরিবেশন করে।
নিন্দুকেরা যা-ই বলুক, ওদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীসুলভ ভালোবাসাও কিন্তু আছে–রাত্রিবেলায় ওরা একে-অন্যকে ‘শুভরাত্রি জানিয়ে যে-যার রুমে চলে যায়! দরজায় তালা দেয়ার কোন বন্দোবস্ত নেই। ফলে, স্বামীকে মাঝে মাঝেই রাত্রিবেলায় স্ত্রীর রুমে যেতে দেখা যায়। তবে, খাটগুলো দুজন থাকার অনুপযুক্ত হওয়ায়, ভোরবেলায় স্বামীকে আবার তার নিজের রুমেই পাওয়া যায়! সকালে স্ত্রীর রুমের দরজায় স্বামীর মৃদু কড়াঘাত–“ওগো! শুভ সকাল। আজ কেমন লাগছে গো?”
–বেশ ভাল গো! তোমার কেমন লাগছে?
সকালে নাস্তার টেবিলে দেখলে মনে হয়, যেন আজই ওদের প্রথম দেখা হল!
সন্ধ্যাবেলায় সাধারণত ওরা বেড়াতে বের হয়। আশেপাশের মানুষজনের বাসায় যায়, গল্প করে। দুজনের বোঝাপড়াটা চমৎকার। একজন-অন্যজনের জন্য ছোটখাটো অনেক কিছুই ছাড় দেয়। যেমন, স্বামী যেদিকেই বেড়াতে নিয়ে যাক স্ত্রী তাতে সায় দেয়, সিগারেটের গন্ধ নিয়ে কোন অভিযোগ করে না। আবার, স্বামীও স্ত্রীর অনেক ছোটখাটো বদ অভ্যাসকে মেনে নেয়। এভাবে, সবার কাছে ওরা ‘আদর্শ দম্পতি’ বলে স্বীকৃত হল। এমন সোনায়-সোহাগা জুটি খুঁজে পাওয়া ভার! তবে, স্ত্রীর বাবা-মা কিন্তু এসব নিয়ে বেশ নাখোশ। তারা শহরের অদূরে গ্রামে থাকেন, মাঝে মাঝে মেয়েকে চিঠি লিখেন। চিঠিগুলোর বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে খানিকটা অশোভন বলেই মনে হয় তারা নাতি-নাতনীর মুখ দেখতে চান প্রতিটি চিঠিতেই তারা লুইসাকে মনে করিয়ে দেন, বিয়ে নামক সামাজিক প্রথাটি টিকে থাকে সন্তান জন্মদানের কারণেই; সন্তানের সুখই বাবা-মায়ের সুখ, সন্তানাদি না-থাকলে বাবা-মা কিছুতেই সুখী হতে পারেন না। কিন্তু লুইসার এতে ভীষণ আপত্তি। তার মতে, এসব ধ্যানধারণা এখন সেকেলে হয়ে গেছে। তবে মা-ও দমবার পাত্রী নন। তিনি উল্টো বলে বসেন, “তোমাদের নতুন ধ্যানধারণাতো বাপু মানব প্রজাতিটিকেই বিলুপ্ত করে দেবে!” এসব কথায় লুইসার বিশেষ কোন ভাবান্তর হয় না। সে এগুলোকে পাত্তাই দেয় না। সে আর তার স্বামী সুখে আছে, এই প্রথম জগৎ কোন সুখী দম্পতি দেখল–এ নিয়ে জগতের তো হিংসা হবেই।
জীবন বয়ে চলে মসৃণভাবে। কেউ কারো প্রভু নয়, দাসও নয়; তারা সমান-সমান। সংসারের খরচাপাতি দুজনে সমানভাবে বহন করে। আজ হয়ত স্বামী বেশি রোজগার করল, তো কাল স্ত্রী বেশি করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংসার খরচে তাদের অবদান ঐ সমান-সমান।
*** *** ***
লুইসার জন্মদিন!
সকালবেলা ঠিকা-ঝি এসে এক হোড়া ফুল, আর নানান আঁকিবুকি করা নকশাদার একটা চিঠি হাতে দিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। চিঠিতে লেখা–
“আমার ভালোবাসার ফুলকুঁড়িকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। অনাবিল আনন্দের এই দিনটি প্রতি বছর বয়ে আনুক আরও বেশি প্রশান্তি। আশা করি, আমার ফুলকুঁড়ি তার আনাড়ি আঁকিয়েকে চমৎকার একটা ব্রেকফাস্টে সঙ্গ দিয়ে ধন্য করবে–এখনই।”
চিঠি পেয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে স্বামীর রুমের দরোজায় কড়া নাড়ল লুইসা।
–কাম ইন…
খাটের ওপর নাস্তা সাজিয়ে দুজন একসাথে নাস্তা করল। ঠিকা-ঝিকে আজ সারাদিনের জন্য বাসায় রেখে দিয়ে নিজেদের মত করে দিনটা কাটাবে ওরা। “আহ! কী চমৎকার একটা দিন!”
এভাবেই দুটি বছর কেটে গেল। তবে, ওদের দেখে কিন্তু তা বোঝার উপায় নেই। এই দু’বছরে ওদের সংসারে কখনোই সুখের কমতি হয়নি। কে বলেছে বিবাহিত জীবন সুখের হয় না? আগের প্রজন্মের সবাই ভুল কথা বলেছে! মনীষীদের বাণী সব বানোয়াট! ওদের বিয়েই হচ্ছে আসল বিয়ে।
*** *** ***
দু’বছরেরর মাথায় স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। বারবার বমি করতে থাকল। তার ধারনা, হয় কোন খাবার, না-হয় কোন জিনিসপত্র থেকে জীবাণু সংক্রমণ হয়েছে। স্বামীও সায় দিল,”হ্যাঁ, হ্যাঁ জীবাণুই হবে।” কিন্তু তারপরেও কী যেন কী ঠিক নেই বলে মনে হচ্ছে। তাহলে কি ঠান্ডা লাগল? সর্দিগর্মি? নানান সন্দেহে স্বামী-স্ত্রীর দিনাতিপাত। এদিকে, স্ত্রীর পেটটা দিনদিন একটু-একটু ফুলে যাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে! তবে কি? …
–তবে কি পেটে টিউমার হলো?
ভয়ে আতঙ্কে ঘুম হারাম হলো।
স্ত্রী অবশেষে ডাক্তারের শরণাপন্ন হল। কিন্তু ডাক্তারের কথা শুনে কান্না করতে-করতে বাড়ি ফিরল। হ্যাঁ, ঠিকই আছে, পেটের ভেতরের জিনিসটা দিন-দিন বড় হচ্ছে। সময়ে আরও বড় হবে। তারপর, একদিন আলোর মুখ দেখবে সেটা। ধীরে ধীরে পরিণত হবে। এরপর, একদিন হয়তো বংশধরও সৃষ্টি করবে–“মা হতে চলেছে লুইসা!”
স্বামীর অনুভূতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন হল। একরকম অদ্ভুত আনন্দ হল তার। ক্লাবে গিয়ে বন্ধুদের কাছে খুব গর্ব করে বেড়ালো। তবে স্ত্রীর কান্না যেন থামতেই চায় নাঃ নিজেকে নিয়ে ভীষণ দুঃশ্চিন্তা হল, এখন তার অবস্থান নীচু হয়ে যাবে যে! কিছুদিন পর থেকেই তো আর উপার্জন করতে পারবে না। তখন যে তাকে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হবে! তাছাড়া, কাজ করতে পারবে না বলে কাজের লোকও তো রাখতে হবে। অর্থাৎ, কাজের লোকের ওপরও এরকম নির্ভরশীলতা আসবে। “উফ! এত দিনের সমস্ত চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণা এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে?”
ওদিকে, খবর পাওয়ার পর থেকে অনবরত মায়ের চিঠি আসতে লাগলো। প্রতিটি চিঠিতে তিনি ঘুরেফিরে একই কথা ববাঝাতে চেষ্টা করেন–“বিয়ে হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, সন্তান প্রতিপালনে সেটা পূর্ণতা পায়। পিতা-মাতার নিজেদের সুখ এখানে বিশেষ ধর্তব্য নয়।” হুগোও (স্বামী) বারবার অনুরোধ করতে থাকল, স্ত্রী যেন আয়-উপার্জনের ব্যাপারে কখনো মন ছোট করে না থাকে। শিশুর দেখাশোনার জন্য সে যা করবে তা কি কাজ নয়? একে কি টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করা সম্ভব, না উচিত? টাকা-পয়সাতো কাজের মাধ্যমেই আসে। তাহলে কি এ-সংসারে তার অবদানকে কোনভাবে খাটো করা যায়? কখনোই না; বরং আগের মত তারা সমানে-সমানই থাকবে।
তারপরও স্বামীর ওপর নির্ভরশীলতার কথাটা লুইসা কোনওভাবেই মানতে পারছিল না। কিন্তু কোল আলো করে আসা শিশুর কান্না কানে যাওয়ামাত্র অন্য সব কিছুই সে ভুলে গেল।
*** *** ***
আগের মত ‘স্ত্রী’ আর ‘বন্ধু’ দুই পরিচয়েই রইলো লুইসা। সেইসাথে একটা নতুন পরিচয় যোগ হল–সে এখন সন্তানের মা! হুগোর কাছে মনে হল, শেষের পরিচয়টিই সবচেয়ে বেশি মূল্যবান!
প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা
বাবা তাকে বুক-কিপিং এর কাজটা শিখে রাখতে বলেছিলেন, যাতে আর দশটা মেয়ের মত স্বামী-সংসারের প্রতীক্ষায় বসে থাকতে না হয়। এখন সে রেলওয়ে অধিদপ্তরের মালামাল বিভাগে বুক-কিপারের কাজ করে। অফিসের সবাই তাকে একজন যোগ্য কর্মী এবং যোগ্য নারী হিসেবে চেনে। সবার সাথেই সে চমৎকারভাবে মিশতে পারে। সব মিলিয়ে, তার মধ্যে অমিত সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।
একদিন বন বিভাগের এক কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ হল। অল্প কিছুদিনেই দুজনের মধ্যে বেশ বোঝাপড়া হয়ে গেল। কিছুদিন বাদে তারা বিয়ে করল। নতুন দম্পতির চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সিদ্ধান্ত হল, তারা কখনোই সন্তান নেবে না। বিয়ে হচ্ছে একটা আত্মিক বন্ধন; এখানে সন্তান খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। জগৎকে তারা দেখিয়ে দিতে চায়, নারী মানেই ভোগের বস্তু নয়–নারীরও মন আছে।
স্বামী-স্ত্রীর দেখা হয় রাতের বেলা খাবার টেবিলে। নানা আদর্শিক কথাবার্তা হয় তখন। তাদের বিয়েটা তো দুটো আদর্শের মিলন, দুটো আত্মার মিলন। এ মিলনের মধ্যে আদর্শিক কথাবার্তা থাকবে সেটাইতো স্বাভাবিক, তাই না? যাহোক, দেহের মিলনও কদাচিৎ ঘটে, তবে সে ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কখনো কোন কথা হয় না।
স্ত্রী একদিন বাড়ি ফিরে জানালো তার অফিসের সময়সূচি পরিবর্তিত হয়েছে। পরিচালক মহোদয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন থেকে রাতের বেলা মার্লমো পর্যন্ত একটা নতুন ট্রেন চালু হবে। সুতরাং সন্ধ্যে ছ’টা থেকে নটা পর্যন্ত অফিসে থাকতে হবে। স্বামীর জন্য এটা খুবই বিরক্তিকর একটা ব্যাপার হল। কারণ সে নিজে কিছুতেই ছটার আগে বাড়ি ফিরতে পারে না, আর এখন বাড়ি ফিরে দেখতে হবে বউ বাড়িতে নেই। কী আর করা! ‘ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন’–এখন আর একসাথে বসে খাওয়া হয় না, রাতের বেলা অল্প একটু সময়ের জন্য দেখা হয়। স্বামী বেচারার দুঃখের সীমা নেই। সন্ধ্যাবেলার দীর্ঘ সময়টাকে সে এখন রীতিমত ঘৃণা করে।
ধীরে ধীরে অভ্যাসে কিছুটা পরিবর্তন এল। সন্ধ্যাবেলায় সে স্ত্রীর অফিসে গিয়ে বসে থাকে। কিন্তু মালামাল বিভাগে বসে থাকাটা মোটেই সুখকর কোন অভিজ্ঞতা নয়, বিশেষত আসতে যেতে কুলিরা যখন ধাক্কা দিয়ে চলে যায়, তখনতো নয়ই। কীভাবে যেন প্রতিবার সে কুলিদের হাঁটাচলার পথের ওপরেই বসে পরে! যাহোক, এতসব ঝক্কি সামলে স্ত্রীর সাথে একটু আলাপ করার চেষ্টা করামাত্র সে কাঠখোট্টাভাবে বলে ওঠে “ওফ! কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত বিরক্ত কর না।” ধমক খেয়ে বেচারা একেবারে চুপ মেরে যায়, আর লক্ষ করে কুলিরা মুখ ফিরিয়ে হাসছে। কখনোবা স্ত্রীর সহকর্মীদের বলতে শোনা যায়–“মিসেস অমুক, আপনার স্বামী আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।” ‘স্বামী’ শব্দটা ওরা এমনভাবে উচ্চারণ করে যে শুনলেই গা জ্বালা করে। তবে, সবচেয়ে বেশি বিরক্ত লাগে স্ত্রীর পাশের টেবিলের আহাম্মকটাকে দেখলে। গর্দভটা সবসময় স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে; আর, নানা ছুতোয় গপ্পো জমানোর চেষ্টা করে। জমা-খরচের খাতা দেখানোর ছল করে এমনভাবে কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পরে কথা বলে যে একটু হলেই ওর চিবুক তার স্ত্রীর গায়ে লেগে যায়। স্ত্রী অবশ্য এতে কিছু মনে করে বলে মনে হয় না। চালানবই, নথিপত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে গর্দভটার কথোপকথন শুনলে মনে হয় যেন এসব ব্যাপারে সবকিছু তার নখদর্পণে! দুজনকে আলোচনারত অবস্থায়। দেখলে বোঝা যায়, ওরা একে অপরকে বেশ ভালোভাবে জানে; এতটা ভালোভাবে যে, হয়ত স্বামী-স্ত্রী নিজেরাও নিজেদের অতটা ভালোভাবে জানে না। অবশ্য সেটা অযৌক্তিকও নয়; কারণ, স্বামীর সাথে স্ত্রী যতটা সময় কাটায়, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কাটায় ঐ আহাম্মকটার সাথে । তাই, কিছুদিন পর থেকে স্বামীর মনে হতে লাগল–তাদের বিয়েটা আসলে সত্যিকারের আত্মিক বন্ধন নয়, সেটা হত যদি সে নিজেও মালামাল বিভাগে কাজ করত। আফসোস! সে তো কাজ করে বন বিভাগে।
একদিন(অবশ্য রাত বলাটাই ভাললা) স্ত্রী স্বামীকে জানালো, পরের শনিবার রেলওয়ে বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক মিটিং আছে। মিটিং শেষে রাতের খাবারের আয়োজনও থাকবে। সেখানে তাকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। খবরটা শুনে স্বামীর কেমন একটু খচখচানি লাগলো। মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল, “তুমি যাবে?”
“অবশ্যই যাবো” স্ত্রী বেশ জোর দিয়ে বলল।
স্বামী আগের মতই অস্বস্তি নিয়ে রইলো–“কিন্তু এতগুলো পুরুষ মানুষের মধ্যে তুমিই একমাত্র মহিলা। তাছাড়া, জানোতো পুরুষ মানুষের পেটে মদ পড়লে অন্য কিছু আর খেয়াল থাকে না।”
–তুমি তোমার বন বিভাগের মিটিংয়ে আমাকে ছাড়া যাও না?
“অবশ্যই যাই কিন্তু সেখানে আমি একগাদা মহিলার মাঝে একমাত্র পুরুষ হিসেবে থাকি না।” যুতসই জবাব দিতে পারায় স্বামীকে খুশি দেখালো।
স্ত্রী এই ভেবে অবাক হল, তার স্বামী, যে কিনা সবসময় নারীমুক্তির কথা বলে, আজ এমন কথা বলছে! তার মিটিংয়ে যাওয়া নিয়ে আপত্তি করছে! সে কি ভুলে গেছে, নারী আর পুরুষ সমান-সমান?
শেষ পর্যন্ত স্বামীকে হার মানতে হল। স্বীকার করতেই হল, এগুলো তার ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি। এতক্ষণ সে যা বলেছে তার সবই ভুল এবং সর্বোপরি, স্ত্রীর মতামতই সঠিক। কিন্তু সবকিছু মেনে নিয়েও সে স্ত্রীকে বারবার অনুনয় করল না-যাবার জন্য। আসলে ব্যাপারগুলো সে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছে না, আবার মন থেকে মানতেও পারছে না।
“তুমি অযৌক্তিক আচরণ করছ” স্ত্রী বিরক্ত হল।
স্বামী মেনে নিল, তার আচরণগুলো ঠিক যৌক্তিক হচ্ছে না। তবে, এটাও সত্য যে, নতুন এ যৌক্তিকতার সাথে মানিয়ে নিতে কম করে হলেও আরও অন্তত দশটি প্রজন্ম পর্যন্ত সময় লাগবে!
ঠিক আছে, তাহলে স্বামীরও এখন থেকে আর মিটিংয়ে যাওয়া চলবে না।
তা কী করে হয়? দুটো ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ স্বামীর মিটিংগুলোতে শুধুমাত্র পুরুষ মানুষেরাই থাকে। তাছাড়া স্বামীতে স্ত্রীকে মিটিংয়ে যেতে নিষেধ করেনি; যে ব্যাপারটা তার পছন্দ হচ্ছে না তা হল, রাতের বেলায় একা-একা এতগুলো পুরুষ মানুষের সাথে মিটিং করতে যাওয়া।
স্ত্রী মোটেই একা-একা যাচ্ছে না। অফিসের ক্যাশিয়ারের স্ত্রীও যাবে।
কিন্তু কী হিসেবে যাবে?
কেন, ক্যাশিয়ারের স্ত্রী হিসেবে!
তাহলে, স্বামী হিসেবে সে-ও কি যেতে পারে না?
তা হয়তো পারে, কিন্তু এসবের মধ্যে গিয়ে নিজেকে সে একেবারে সস্তা বানিয়ে ফেলবে না?
নিজেকে সস্তা বানাতে স্বামীর কোন আপত্তি নেই।
আচ্ছা, স্বামী কি হিংসা করছে?
অবশ্যই, কেন নয়? তাদের দুজনের মধ্যে অন্য কিছু আসতে পারে এই ভেবে সে রীতিমত আতঙ্কিত হচ্ছে।
ঊহ্! কী লজ্জা! কী অপমান, অবিশ্বাস! কী ঈর্ষা! স্বামী তাকে কী মনে করে?
মনে করে, তার স্ত্রী সম্পূর্ণ নিখুঁত। মনে করে, সে এতক্ষণ যা বলেছে তা ঠিক নয়। স্ত্রী ইচ্ছা করলে মিটিংয়ে যেতে পারে।
বাহ্! কী অবলীলায় স্বামীর আত্মবনমন!
স্ত্রী মিটিংয়ে গেল। শেষ করে বাড়ি ফিরতে ভোর হয়ে গেল। ফিরেই স্বামীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বেশ উচ্ছ্বাস নিয়ে জানালো, সবকিছু খুব ভালোভাবে শেষ হয়েছে। স্বামী মৃদু হাসলো। উৎসাহ পেয়ে স্ত্রী আরও নানান খুঁটিনাটি বলতে লাগলো–কেউ একজন তার প্রশংসা করে বক্তৃতা দিয়েছে, তারা সবাই একসঙ্গে গানে গলা মিলিয়েছে এবং শেষ পর্যায়ে, তাদের সমবেত নৃত্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটেছে।
কিন্তু এই ভোরবেলা স্ত্রী বাড়ি ফিরল কীভাবে?
কেন? ওই বেআক্কেলটা পৌঁছে দিয়ে গেছে।
কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলত!
তাহলেই বা কী হত? নিঃসন্দেহে সবাই তাকে একজন সম্মানিত নারী হিসেবেই চেনে, তাই না?
হ্যাঁ, তা ঠিক আছে; কিন্তু কেউ যদি সত্যিই দেখে ফেলত তাহলে কিন্তু সম্মানহানি ঘটত।
আসলে এসব কিছুই না, সত্যি কথাটা হল–স্বামীর ঈর্ষা হচ্ছে, তাই না? আর তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, স্বামী তাকে হিংসা করছে। সে আসলে স্ত্রীর প্রতিটি ছোটখাটো আনন্দকেই হিংসা করে।
এই তাহলে বিয়ের আসল অর্থ? স্ত্রী বাড়ির বাইরে গেলে, সামান্যতম মজা করলেও তাকে কথা শুনতে হবে? উহ! বিয়ে আসলে কী? বিয়ে আসলে নিতান্ত অর্থহীন, নির্বোধ একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান।
কিন্তু তাদের মিলনকে কি সত্যিকার অর্থে বিয়ে বলা যায়? তাদের ঘনিষ্টতা হয় শুধুমাত্র রাতের বেলা; যেমনটি আর দশটা সাধারণ দম্পতিরও হয়। তাহলে, কিসের ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে অন্যরকম মনে করে? তার স্বামীতে দেখা যাচ্ছে আর দশটা সাধারণ স্বামীর মতই চিন্তা করে।
কী আর করা যাবে? সব পুরুষই একরকম! বিয়ের আগে পর্যন্ত তারা সভ্য থাকে, কিন্তু বিয়ের পর… উহ্! বিয়ের পর…! তার স্বামীও অন্যদের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। স্ত্রীকে সে নিজের সম্পত্তি মনে করে, মনে করে, সে চাইলেই যখন-তখন স্ত্রীকে আদেশ করতে পারে! স্বামী আর আগের মত নেই
হয়ত তাই! একটা সময় ছিল যখন স্বামী মনে করত, তারা একে অন্যের; কিন্তু চিন্তাটায় আসলে মস্ত ভুল ছিল। সে হয়ত তার স্ত্রীর, কিন্তু তেমনই যেমন থাকে একটা কুকুর তার মনিবের! সে তার স্ত্রীর ভৃত্য বৈ অন্য কিছুতো নয়, যাকে রাখা হয় কেবল রাতের বেলা বাড়ি পাহারা দেবার জন্য। সে হয়ত ‘স্ত্রীর স্বামী, কিন্তু স্ত্রী কি কখনো স্বামীর স্ত্রী হবার চেষ্টা করেছে? তারা দুজন কি আসলেই সমান-সমান?
এ-জাতীয় কথা শুনে স্ত্রীর মেজাজ চটে গেল। ঝগড়া করার জন্য সে বাড়ি ফেরেনি। সে কখনোই স্ত্রী ভিন্ন অন্য কিছু হতে চায়নি, কিংবা, স্বামীকেও স্বামী ভিন্ন অন্য কোন রূপে পেতে চায়নি চিৎকার করে সে এসব কথা বলতে থাকল।
স্বামী মনে মনে ভাবল, স্ত্রী হয়ত মাতলামির ঝেকে এসব কথা বলছে। তাই কোন প্রত্যুত্তর না-করে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল।
স্ত্রী এবারে কান্না জুড়ে দিল। স্বামীকে অনুরোধ করল একটু বোঝার চেষ্টা করতে, ক্ষমা করে দিতে। কিন্তু স্বামী সেসবে কান না-দিয়ে কম্বলে মাথা ঢেকে শুয়ে রইল। স্ত্রী শেষমেষ জিজ্ঞেস করে বসল–“তোমার কাছে কি আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে? আমাকে আর স্ত্রী হিসেবে চাও না?”
অবশ্যই, স্বামী অবশ্যই তাকে স্ত্রী হিসেবে চায়। আসলে, গতকাল সারাটা সন্ধ্যা আর রাত এত একঘেয়ে লেগেছে যে, তার মনে হয়েছে, জীবনে এত খারাপ সময় বোধহয় কখনো আসেনি।
“আচ্ছা, ঠিক আছে, চল আমরা সবকিছু ভুলে যাই।” স্ত্রীর স্বপ্রণোদিত প্রস্তাব।
স্বামীও সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নিল। আবার তারা একে-অন্যকে ভালোবেসে দিনাতিপাত করতে লাগলো।
পরদিন সন্ধ্যায় স্ত্রীর অফিসে গিয়ে জানা গেল, কিছু টুকিটাকি কাজ সারতে স্ত্রী গুদাম ঘরে গেছে। সুতরাং স্বামী বেচারা একা একা বসে রইল। হঠাৎ করে বাইরে থেকে রুমের দরজা খুলে গেল। সেই আহাম্মকটা দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে জিজ্ঞেস করল, “অ্যানী রুমে আছ নাকি?”
অ্যানীর স্বামীকে দেখে হকচকিয়ে গিয়ে সাট করে সরে পড়ল হতভাগাটা। স্বামীও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। গর্দভটা তার স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকে; তার মানে, দুজনের মধ্যে বেশ ভালোরকম ঘনিষ্টতা আছে। এতটা ঘনিষ্টতা সহ্য করা স্বামীর পক্ষে কষ্টকর। কাউকে কিছু না-বলে সে চুপচাপ বাড়ি ফিরে এলো। পরবর্তীতে, এ-নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটিও হল একচোট। স্ত্রীর অভিযোগ–নারীমুক্তির ব্যাপারটা তার স্বামী আসলে কখনোই মন থেকে মেনে নেয়নি, নিলে সহকর্মীর সাথে স্ত্রীর ভালো সম্পর্ক হওয়াটাকে সে খারাপ চোখে দেখতে পারত না। পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হল যখন স্বামী বলে বসল–“আগেকার কথা নিয়ে অত ঘাটাঘাটি করে লাভ নেই।”
“মানে কী? তুমি নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তে কথা বলছ না। তুমি নিশ্চয়ই আগেকার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলনি?”
ফেলেছে, স্বামী তার আগেকার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলেছে। কারণ, জীবন নিয়ত পরিবর্তনশীল, আর এই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনটাও আবশ্যক। তবুও যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, বিয়ে বলতে ‘আত্মিক বন্ধন’র সেই ব্যাপারটা সে এখনো বিশ্বাস করে কি না, সে জবাব দেবে–বিয়ে ব্যাপারটাতেই এখন আর তার বিশ্বাস নেই; তা সে যে ধরনের বন্ধনই বোঝাক না কেন। ব্যাপারটার আসলে আমূল সংস্কার প্রয়োজন। তাছাড়া, যদি আত্মিক বন্ধনের কথাই বলা হয়, তাহলে তো বলতে হয়, তার স্ত্রী ঐ গর্দভটার সাথে আত্মিক বন্ধনের সূত্রে বিবাহিত! কারণ, প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলে, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াটাও ভাললা; অথচ, স্বামীর বন বিভাগ নিয়ে কিন্তু স্ত্রীর নূ্যনতম আগ্রহ নেই। তাহলে কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আত্মিক কিছু আছে বলা যায়? সত্যিই কি তাদের মধ্যে কোন বন্ধন দাবি করা যায়?
না, যায় না। অন্তত, এখন আর দাবি করা যায় না। স্বামী যখন ‘নারীমুক্তি বিষয়ে নিজের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করেছে, তখনই সে এই দাবিকে নিজের হাতে খুন করেছে। স্ত্রী অন্তত তা-ই মনে করে।
*** *** ***
সংসার এখন আরও বেশি অসহনীয় হয়ে উঠেছে। মালামাল বিভাগের চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে স্বামী এখন তার বন বিভাগের সহকর্মীদের সঙ্গ খুঁজে নেয়। যে বিভাগের কাজকর্ম সে বোঝে না, সে বিভাগের কোন কিছু নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ওদিকে স্ত্রী প্রায়ই বলে, “তুমি আমাকে আর বোঝ না।”
“আমি মালামাল বিভাগটাকে বুঝি না” স্বামীর ঠাণ্ডা প্রতিবাদ।
*** *** ***
এক রাতে (অবশ্য সকাল বলাটাই ভালো) স্বামী জানালো, পরদিন তাকে উদ্ভিদবিদ্যার ব্যবহারিক ক্লাস নিতে যেতে হবে। মেয়েদের একটা স্কুলে উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাস নেয়ার দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর।
আচ্ছা! তাই নাকি? তো, এ-কথা আগে বলেনি কেন?
বলা হয়ে ওঠেনি।
তা, মেয়েদের’ বলতে কি বড় মেয়েদের?
হ্যাঁ, ষোল থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে হবে।
সকালবেলাই যেতে হবে?
না, বিকেলে। ক্লাস শেষে রাতের খাবারের আয়োজনও থাকবে। মেয়েরা নাকি আশেপাশের কোন গ্রামে গিয়ে রাতে খাবার খাওয়ার বায়না ধরেছে।
তাই নাকি? স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাও সাথে থাকবেন নিশ্চয়ই?
না, উনি থাকবেন না। বন বিভাগের কর্মকর্তার ওপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা আছে। কর্মকর্তাটি যেহেতু বিবাহিত, তার ওপর এতটুকু আস্থা রাখাই যায়।
হুম, বিবাহিত হবার কিছু সুবিধাও আছে তাহলে!
পরদিন সকালে স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। স্বামী নিশ্চয়ই অসুস্থ স্ত্রীকে ফেলে বাইরে যাবার মত এতটা নির্দয় হবে না?
কিন্তু স্বামীকে তো সবার আগে নিজের কাজের কথা চিন্তা করতে হবে, তাই না? স্ত্রী কি খুব বেশি অসুস্থ?
হ্যাঁ, ভীষণ।
স্ত্রীর বাধা সত্ত্বেও ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার এসে জানালো “দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই, এমনিতেই হয়ত একটু খারাপ লেগেছে, আবার এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে।” অতএব, স্বামীর বাড়িতে বসে থাকার কোন মানে হয় না। সে নির্দ্বিধায় ব্যবহারিক ক্লাস নিতে চলে গেল। ক্লাস শেষ করে বাড়ি ফিরতে ভোর হয়ে গেল। অথচ, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ক্লান্তির ছাপ নেই। উপরন্তু, তাকে বেশ টগবগে দেখাচ্ছে। অনেক দিন পর খুব চমৎকার একটা দিন পার করেছে সে, অ…নে…ক দিন পর।
“উঁহুহুহু…” এতক্ষণ চেপে রাখা আবেগ এবার কান্না হয়ে স্ত্রীর চোখেমুখে ঝড় তুলল। এত দূর সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়–স্বামীকে এখন প্রতিজ্ঞা করতেই হবে যে, তাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে সে কখনো ভালোবাসবে না, কক্ষনো না।
তুমুল কান্নাকাটির এক পর্যায়ে, স্ত্রী হঠাৎ মৃগী রোগীর মত ছটফট করতে লাগল। স্বামী দৌড়ে গেল স্মেলিং সল্ট আনতে। খানিক পর স্ত্রী একটু স্বাভাবিক হলে, একটু-একটু করে তাকে নানা কথা বলতে লাগল। মেয়েদের সাথে রাতের খাবারের খুঁটিনাটি বিবরণ না-দিলেও, অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে কথা হল তাদের মধ্যে। স্ত্রী যখন অতগুলো পুরুষ মানুষের মাঝে রাত্রিবেলায় মিটিংয়ে গিয়েছিল স্বামীর তখন কেমন লেগেছিল সে কথাও বলল। স্ত্রী এখন কান্না করছে কেন? কোন বিষয়টা তাকে কাঁদাচ্ছে? সে নিশ্চয়ই ঈর্ষা করছে না? নাকি করছে? অধিকারবোধটা যদি দুদিক থেকেই কাজ না-করে তাহলে সেটা সত্যিকারের ভালোবাসাই নয়। স্বামীর ওপর অধিকারবোধ কাজ করেছে বলেই নিশ্চয়ই তাকে হারানোর ভয়ে স্ত্রী এখন কাঁদছে? কারণ, হারানোর ভয়টা অধিকারবোধ থেকেই আসে। স্বামীরও কিছুদিন আগে ঠিক এই কারণেই অমন খারাপ লেগেছিল।
এভাবেই, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার বেশ কিছুদিনের জমে থাকা ভুল বোঝাবুঝি আপাত ঠিকঠাক হল। তবে, চিড় ধরানোর জন্য মালামালের বিভাগ আর মেয়েদের স্কুল কিন্তু কাঁচি নিয়ে তৈরি হয়েই ছিল!
*** *** ***
কিছুদিন পর একটা বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর প্রশান্তিতে আবারও ছন্দপতন হল–
স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার ধারণা, সেদিন অফিসে লেবারদের কাজে যেচে সাহায্য করতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটেছে। লেবাররা সেদিন কতগুলো ভারী বাক্স ওঠাচ্ছিল। তার নিজের সামনেও পড়ে ছিল একটা। লেবারদের অপেক্ষা না-করে, অতি উৎসাহী হয়ে সে একাই উঠাতে গিয়েছিল ওটা। ফলস্বরূপ, আজ বিছানায়।
কিন্তু ঘটনা কি আসলেই তাই?
উঁহু ঘটনা অন্য জায়গায়!
সে ঘটনা জানতে পেরে স্ত্রী ভীষণ রেগে গেল, আর পুরো দোষটা চাপালো স্বামীর ঘাড়ে। বাচ্চাটাকে নিয়ে এখন কী করবে তারা? “ওকে তো বোর্ডিংয়ে মানুষ করতে হবে!”
হ্যাঁ, রুশো (স্বামী) একাই এজন্য দায়ী! রুশোটা আসলে আস্ত বোকা, না-হলে এমন কাজ কেউ করে? যাহোক, স্বামী হিসেবে সমস্ত দোষ মাথা পেতে নিতে সে মোটেও আপত্তি করল না; বরং ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরবর্তীতে আর কখনো মেয়েদের ক্লাস না-নেয়ার প্রতিজ্ঞা করল। তবে, এতকিছুর পরও স্ত্রীর বিরক্তিভাব কমেনি। সে এখন আর গুদাম ঘরে যেতে পারবে না ভাবতেই গা জ্বলছিল। এখন থেকে বাধ্য হয়ে তাকে অফিসের সামনের রুমে বসে মালামালের হিসাব লিখে রাখার কাজ করতে হবে। কিন্তু এসব কিছুর বাইরেও সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার যেটা ঘটল সেটা হল, এক সহকারীর আবির্ভাব, যার গোপন অভিসন্ধি ছিল যেকোনভাবে অফিসে স্ত্রীর চেয়ারটা দখল করা।
অফিসে সহকর্মীদের আচরণ আজকাল কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। এমনকি লেবাররাও তার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসে। স্ত্রী ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে যায়। মনে হয়, কোথায় যে লুকাবে তাই যেন ভেবে পায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এখানে বসে মানুষের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হওয়ার চেয়ে বরং ঘরে বসে স্বামীর জন্য রান্নাবান্না করাও ভালো। “উফ! মানুষগুলোর মনে কত রকম আজেবাজে চিন্তা যে থাকে! আর ভালো লাগে না।”
গত একমাস যাবত স্ত্রী বাড়িতে রয়েছে। অফিসে যাওয়া এখন প্রায় অসম্ভব ঠেকছে। সে এখন প্রায় সবসময়ই ক্ষুধার্ত থাকে। সকাল হতে-না হতেই তার জন্য স্যান্ডউইচ আনাতে হয়। শরীরটা সারাক্ষণ কেমন যেন ঝিমঝিম করে। মনে হয়, যেন যেকোন সময় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। ফলে, বেশিরভাগ সময়ই বিশ্রাম নিতে হয়। কী একটা জীবন! কষ্টই বোধ হয় মেয়েমানুষের ভাগ্যের লিখন।
*** *** ***
অবশেষে সেই দিনটি এল। তাদের সন্তান আলোর মুখ দেখলো।
বাচ্চার বাবার জিজ্ঞাসা–“এখন কি আমরা ওকে বোর্ডিংয়ে রেখে আসবো?”
“ছিঃ, পুরুষ মানুষের কি হৃদয় বলে কিছু নেই?”
সন্দেহ নেই, বাচ্চার বাবার হৃদয়জাতীয় কিছু একটা আছে! অতএব, বাচ্চা বাড়িতেই বড় হতে লাগলো।
এর পর, একদিন অফিস থেকে এল এক অমায়িক চিঠি: বাচ্চা এবং বাচ্চার মা ভালো আছে তো?
হ্যাঁ, তারা দুজনেই ভালো আছে, এবং আগামী পরশুদিন বাচ্চার মা আবার অফিসে ফিরবে।
তবে, সত্যিকারে বাচ্চার মা এখনো কিছুটা দুর্বল রয়ে গেছে; যে কারণে তাকে গাড়ি ভাড়া করে অফিসে যেতে হয়। অবশ্য, খুব শীঘ্রই সে শরীরে বল ফিরে পেতে শুরু করল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়: বাচ্চাটার সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখতে হয়। অবশ্য, শীঘ্রই সুবিধাজনক একটা বুদ্ধিও বের হল–বাচ্চার খোঁজ-খবর জানাতে একটা ছেলেকে নিয়োগ দেয়া হল। প্রথমদিকে ছেলেটাকে বাড়িতে পাঠানো হত দিনে দু’বার; কিছুদিন পর থেকে, প্রতি দু’ঘণ্টা পর-পর। বাচ্চার মা যখনই শুনে বাচ্চা কাঁদছে, তৎক্ষণাৎ সবকিছু ফেলে বাড়ি ছুটে যায়। ওদিকে, অফিসে তার পদটি দখলের চিন্তায় একজন তো আছেই। তবে তার বিভাগীয় প্রধান বেশ সদয় ব্যক্তি, এই যা বাঁচোয়া।
*** *** ***
বাচ্চার মা একদিন আবিষ্কার করল–বাড়ির নার্সটা ঠিকঠাকমত বাচ্চার দেখাশোনা করতে পারছে না। বাচ্চাকে খাওয়ানোর মত যথেষ্ট বুকের দুধ তার নেই; অথচ, চাকরি হারানোর ভয়ে এ-কথা সে এতদিন গোপন রেখেছে। অগত্যা, একদিনের ছুটি নিতে হল। নতুন নার্স খোঁজ করা হল। কিন্তু তেমন সুবিধা করা গেল না। সবগুলো আসলে একই রকম–শুধু নিজের স্বার্থ বোঝে। অন্যের বাচ্চাকে যত্ন নিয়ে খাওয়াতে চায় না। এগুলোর কোনটার ওপরই আস্থা রাখা যায় না।
“না, মোটেই আস্থা রাখা যায় না” বাচ্চার বাবাও সহমত পোষণ করলো। “এক্ষেত্রে একমাত্র নিজে ছাড়া অন্য কাউকেই ভরসা করা যায় না।”
বাচ্চার মা সরু চোখে তাকালো–“মানে কী? তুমি কি আমাকে চাকরি ছাড়ার ইঙ্গিত করছ?”
–উঁহু, তোমার যেমন ভালো মনে হয় তুমি তেমনই করবে।
–সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে তোমার দাসী হয়ে যাই সেটাইতো সবচেয়ে ভালো, তাই না?
–মোটেও না, আমি মোটেই সে রকম কিছু বলিনি।
বাবা-মায়ের কথা কাটাকাটির মধ্যে পরে বাচ্চার অবস্থা দিন-দিন আরও খারাপ হতে থাকলো। নানান অসুখবিসুখে ভুগতে লাগলো।
ও কিছু না, সব বাচ্চাই অসুখে ভোগে।
কিন্তু এসব বলে মনকে আর কতক্ষণ প্রবোধ মানানো যায়? অতএব, বাচ্চার মাকে প্রায়ই ছুটি নিতে হয়। সম্প্রতি বাচ্চার মাড়ি ব্যথা হয়েছে।
ব্যথায় জ্বর এসে গেছে। ফলে, আরও একদিন ছুটি নিতে হল। ব্যথা তেমন। কমছে না। রাত জেগে নানা কায়দা করে ওকে ঘুম পাড়াতে হয়, তারপর দিনে আবার অফিস: ক্লান্তি, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, দুঃশ্চিন্তা এবং …
আরও একটা দিন ছুটি নেয়া।
বাচ্চার বাবা তার সাধ্যমত বাচ্চার দেখাশোনা করে। অর্ধেক রাত পর্যন্ত বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রাখে, ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কখনোই মালামাল বিভাগের কাজকর্ম নিয়ে কোন কথা বলে না।
তারপরও স্ত্রীর মনে হয়, সে জানে স্বামী আসলে ঠিক কী চায়–স্বামী চায়, চাকরিটা সে ছেড়ে দিক। স্বামী যদিও ঘুণাক্ষরেও কখনো এ ধরনের কোন কথা তাকে বলেনি, তবুও কেন যেন তার মনে অশান্তি বাড়তে থাকে: “উফ! পুরুষ মানুষগুলো কী পরিমাণ বিশ্বাসঘাতক!” স্বামীকে সে ঘৃণা করে। সে আত্মঘাতী হবে, তবু চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বামীর দাসী হবে না।
ওদিকে, মুখে কিছু না বললেও বর্তমান পরিস্থিতি দেখে একটা ব্যাপার স্বামী খুব ভালো বুঝতে পেরেছে–“যত যাই বলা হোক না কেন, প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় আইন থেকে কারোরই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।”
*** *** ***
দিনদিন সংসার খরচ বাড়ছে। বাচ্চার বয়স যখন পাঁচ মাস পড়ল, তখন খরচ সামলাতে স্বামীকে আবারও মেয়েদের স্কুলে পড়ানোর কাজটা শুরু করতে হল। আর, এর মধ্যেই স্ত্রী একদিন নিজেকে পরাজিত ঘোষণা করলো–“আমি এখন থেকে তোমার দাসী হয়ে গেলাম”, চাকরিচ্যুতির কাগজটা তার হাতে ধরা ছিল। “আমাকে এখন থেকে তোমার ইচ্ছামত চলতে হবে।” যদিও পুরো বাড়ির কত্রী সে-ই!
স্বামী নিজের উপার্জিত প্রতিটি টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। সিগারেট খাওয়া বা অন্য যেকোন কাজের জন্য টাকা দরকার হলে স্ত্রীর কাছে টাকা চাইবার আগে সে এক বিশাল ফিরিস্তি দেয়। স্ত্রী অবশ্য কখনোই টাকা দিতে অমত করে না। তবুও, কোন রকম ফিরিস্তি না-দিয়ে টাকা চাইতে তার অস্বস্তি লাগে।
স্বামী এখন মিটিংয়ে যেতে পারে, তবে রাতে সেখানে খাওয়ার অনুমতি নেই, এবং মেয়েদের উদ্ভিদবিদ্যা শেখানোর সবরকম ক্লাস কঠোরভাবে নিষিদ্ধ! সে অবশ্য এখন এমনিতেই ওগুলো আর মিস করে না। কারণ, ছেলের সাথে খেলা করতেই এখন তার বেশি ভালো লাগে। সহকর্মীরা স্ত্রৈণ বললেও কিছু মনে করে না; বরং, হাসিমুখে মেনে নেয়; আর মনে মনে ভাবে স্ত্রীর মধ্যে চমৎকার একজন বন্ধু খুঁজে পাওয়া গেছে।
ওদিকে, স্বামী যত যা-ই বলুক-না-কেন, স্ত্রী কিন্তু একগুয়েভাবে বলতেই থাকে–“আমি তোমার দাসী হয়ে গেলাম!”
হোক, বা না-হোক, অন্তত কথা শোনাতেই আনন্দ!
হায়রে নারীমুক্তি!
ফিনিক্স
ছেলেটা যখন প্রথমবার পাদ্রির বাড়িতে মেয়েটাকে দেখল তখন সময়টা খুব সুন্দর ছিল। বুনো স্ট্রবেরিগুলোতে সবেমাত্র রং ধরেছে। এর আগেও ও অনেক মেয়ে দেখেছে; কিন্তু এমন কখনো মনে হয়নি। কেমন বুকের মধ্যে ধুকপুক করা, কেমন শিহরণ বয়ে যাওয়া–একেই বোধহয় প্রেম’ বলে! মুখ ফুটে বলার মত সাহস তখনো হয়নি, অথচ মেয়েটা কিন্তু ঠিকই ওকে ‘স্কুলবয়’ বলে খ্যাপাত।
দ্বিতীয়বার যখন দেখা হল, ছেলেটা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। আগের চেয়ে সাহস বেড়েছে। ফলে দূরত্ব কমেছে। মেয়েটাকে ও জড়িয়ে ধরল, চুম্বন করল। তখন মনে হল, যেন চারপাশে আতশবাজি ফুটছে, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে, বিউগলের সুরে চারদিক মুদ্রিত হচ্ছে, পায়ের নিচের দুনিয়া যেন থরথর করে কাঁপছে।
মেয়েটার বয়স ১৪। শরীরে সবেমাত্র যৌবনের আনাগোনা। তার নিটোল কটিদেশ, ছন্দোবদ্ধ চলন, চারপাশে এক যাদুকরী মোহময়তা সৃষ্টি করে। বিশুদ্ধ মধুর মত স্বর্ণালী চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যখন বুক আর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ে, মনে হয় যেন জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বলতা ঠিকরে বেড়ুচ্ছে। চোখদুটো যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যে-কেউ সে চোখে চোখ রাখলে মতিভ্রম হতে বাধ্য। মোলায়েম ত্বক যেন ঘুঘু পাখির মতই কোমল। ছেলেটার মনে হয়, ও যেন কোনো মর্তবাসী অপ্সরী।
দুজনের বাগদান হয়ে গেল। সারাদিন ওরা পাখিদের মত কলকাকলিতে মুখরিত থাকে। জীবন যেন সবুজ ঘাসে মোড়ানো এক উদ্যান, যার একটি ঘাসও এখনও মাড়ানো হয়নি। হেসেখেলে দিন যায়। কিন্তু ছেলেটির লেখাপড়া এখনও শেষ হয়নি; বিশেষত খনিজ বিষয়ক পরীক্ষায় এখনও পাশ করা হয়নি। পরীক্ষায় পাশ করা, উচ্চতর গবেষণায় দেশের বাইরে যাওয়া ইত্যাদিসহ সবকিছু মিলিয়ে আরও প্রায় দশ বছর লাগবে। দ…শ বছর। অতএব, বিয়েটা দশ বছর পরেই হবে। এরকম পরিকল্পনা মাথায় নিয়েই ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গেল।
গ্রীষ্মের ছুটিতে ছেলেটি আবারও সেই পাদ্রির বাড়িতে ছুটে গেল, প্রিয়তমার সাথে দেখা করল। প্রিয়তমা ঠিক আগের মতই আছে–কানায় কানায় পূর্ণ অটুট সৌন্দর্য। দেখে প্রাণটা ভরে গেল। কয়েকদিন পর ছুটি শেষ করে ছেলেটি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গেল। এভাবে পর পর তিনটি গ্রীষ্মে প্রিয়তমাকে একইভাবে পেল। কিন্তু চতুর্থবার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা গেল–প্রিয়তমার নাকের গোড়ায় ছোট ছোট লাল দাগ, কাঁধটাও যেন খানিকটা ঝুলে পড়েছে।
ষষ্ঠ গ্রীষ্মে, প্রিয়তমার ভীষণ দাঁত ব্যথা; সেই সঙ্গে স্নায়ুবিক দুর্বলতা। এগুলো তাকে ভীষণ কাবু করে ফেলল। চুলের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে গেল, কণ্ঠস্বর কেমন কর্কশ হয়ে গেল, নাকের চারপাশ কালো-কালো দাগে ভরে উঠলো, চোয়াল বসে গেল। সর্বোপরি, চরম স্বাস্থ্যহানি ঘটল। সে বছর শীতে কাঁপুনি জ্বরও হল। ডাক্তারের পরামর্শে চুল কেটে ফেলতে হল। চুলগুলো যখন আবার বড় হল, দেখা গেল সেগুলো আর আগের মত উজ্জ্বল নেই, কেমন মলিন হয়ে গেছে।
ছেলেটি প্রেমে পড়েছিল এক স্বর্ণকেশীর। সে স্বর্ণকেশীর মলিন কেশ এখন আর আকর্ষণ করে না তাকে। তাই বলে সে কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতাও করল না। চব্বিশ বছর বয়স্কা সেই মলিনকেশীকেই সে বিয়ে করল, যার উচ্ছ্বাস এখন অনেকটা ভাটার দিকে, যে এখন একটু বড় গলার জামা পড়তে অস্বস্তি বোধ করে। এসব মেনে নিয়েও ছেলেটি মেয়েটিকে ভালোবাসে। ভালাবাসার আবেগ অনেকটা কমে গেছে এই যা। বরং, সেখানে দায়িত্ব ভর করেছে। এই দায়িত্বপূর্ণ ভালোবাসা নিয়েই ওরা বেশ সুখে দিন কাটায়। খনির ছোট শহরটার কোন কিছুই ওদের সুখে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না।
সংসারে একে-একে দুটো পুত্র সন্তানের আগমন ঘটলো। স্বামী অবশ্য মনে-মনে কন্যার আশা করছিল। একদিন সে আশাও পূর্ণ হলো। চকচকে চুলের এক কন্যা সন্তান এলো তাদের সংসারে। মেয়ে যেন বাবার চোখের মণি। যত দিন যায় সে দেখতে তত তার মায়ের মত হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে ওর বয়স যখন আট হল, দেখলে মনে হয় যেন ওর মায়ের আট বছর বয়সের কোন ছবি। এই ছোট্ট মেয়েটির জন্য বাবা তার সমস্ত অবসর সময়গুলো উৎসর্গ করেন।
কন্যার মা সারাদিনই ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকেন। ঘর-গৃহস্থালির কাজ করতে-করতে তাঁর হাতে, কপালের কাছে, ভাঁজ পড়ে গেছে। রান্নাঘরে ক্রমাগত উবু হয়ে বসে কাজ করায় কাঁধও ঝুলে পড়েছে। এভাবেই, সংসারে তিনি একেবারে থিতু হয়ে গেছেন। স্বামীর সঙ্গে মন খুলে দুটো কথাও বলা হয় না। দুজনের দেখা হয় কেবল খাবার টেবিলে, আর রাতের বেলা। অবশ্য, এসব নিয়ে তাদের কোন অভিযোগও নেই–সত্যিটা তো এমনই, জীবনের গতি বদলায়।
*** *** ***
বাবার জীবনের একমাত্র সুখ তাঁর কন্যা। মনে হয়, বাবা যেন মেয়ের প্রেমে পড়েছেন! মেয়ের মধ্যে তিনি মেয়ের মায়ের ছায়া খুঁজে পান। মেয়ের মাকে প্রথম দেখে যে অনুভূতি হয়েছিল, মেয়েকে দেখেও তড়িৎ সে অনুভূতি খেলে যায়। যে-কারণে মেয়ের উপস্থিতিতে বাবা বেশ সচেতন আচরণ করেন। মেয়ের পোষাক-আশাক পরিবর্তনের সময় কখনো তার রুমে যান না। সর্বোপরি, মেয়েকে যেন পরম শ্রদ্ধায় পূজা করেন তিনি।
এক সকালে মেয়ে হঠাৎ বিছানায় পড়ল। উঠে দাঁড়ানোর কোন লক্ষণ নেই। মা ভাবলেন মেয়েকে আলসেমিতে পেয়েছে। তাই তেমন গা করলেন না। বাবা কিন্তু দুঃশ্চিন্তায় পড়লেন। তড়িঘড়ি করে ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার যা বললেন তাতে সমস্ত বাড়ি মৃত্যুপুরীর মত নীরব হয়ে গেল। “ডিপথেরিয়া”। এমতাবস্থায়, অন্য বাচ্চাগুলো এখানে থাকলে ওদেরও সংক্রমিত হবার আশঙ্কা আছে। অতএব, অন্য সন্তানদের নিয়ে বাবা কিংবা মায়ের যেকোন একজনকে কিছুদিন দূরে কোথাও থাকতে হবে। বাবা মেয়েকে ছেড়ে থাকতে রাজি নন। সুতরাং, সন্তানদের নিয়ে মা শহরের অন্য প্রান্তে একটা ছোট ঘর ভাড়া করলেন, আর বাবা রইলেন মেয়ের সেবাযত্ন করতে। মেয়ে কিন্তু বিছানাতেই পড়ে রইল।
ঘরজুড়ে সালফারের গন্ধে টেকা দায়। বাঁধানো ছবিগুলো সালফারের তীব্রতায় কালচে হয়ে গেল, ড্রেসিং টেবিলের পেছনের রূপার প্রলেপও জায়গায়-জায়গায় ক্ষয় হল। আর নীরবে ক্ষয় হতে থাকলো মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন। কান্না বুকে চেপে রেখে শূন্য ঘরে পায়চারি করেন বাবা। রাতে একা বিছানায় যন্ত্রণায় ছটফট করেন। নিজেকে বিপত্নীক বলে মনে হয় তাঁর। কিন্তু মেয়েকে এসবের কিছুই বুঝতে দেন না। মেয়ের জন্য নানা খেলনা কিনে আনেন, পুতুলনাচ দেখান, আরও কত কি! এসব দেখে মেয়ে তাঁকে শুষ্ক হাসি উপহার দেয়। সেই হাসিতেই বাবার ক্ষণিক-আনন্দ। মাঝে মাঝে সামান্য সময় বের করে মেয়ের মা-ভাইদের দেখতে যান। কিন্তু পাছে ওরা আবার সংক্রমিত হয়, এই ভয়ে কাছে যান না, দূর থেকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, সন্তানদের চুম্বন ছুঁড়ে দেন। তাঁর স্ত্রী লাল নীল কাগজে লিখে লিখে দূর থেকেই নানা খোঁজখবর জানান।
হঠাৎ একদিন পুতুলনাচের প্রতি মেয়ের আর আগ্রহ দেখা গেল না। তার মুখের হাসি বন্ধ হল, বন্ধ হল মুখের কথাও। অস্থি-চর্মসার শরীরটা থেকে শেষ অনুভূতিটুকুও কেড়ে নিল নিকষ কালো মৃত্যু। দীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান হল।
অতঃপর সন্তানদের নিয়ে মা বাড়ি ফিরে এলেন। তার অনুশোচনার সীমা রইলো না। কারণ সন্তানের মৃত্যুকালে তিনি কাছে থাকতে পারেননি। সমস্ত বাড়ি যেন শোকে-যন্ত্রণায়-হতাশায় বিদ্ধ হয়ে রইল। ডাক্তার এসে লাশের ময়নাতদন্ত করতে চাইলে বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি চান না তাঁর মেয়ের শরীর ছুরি-কাঁচি দিয়ে কাটাকুটি করা হোক। কারণ, তাঁর কাছে মেয়ে এখনও জীবন্ত। ডাক্তার সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। বাবা ভীষণ রেগে গেলেন: চিৎকার-চাচামেচি করে, ডাক্তারকে এলোপাথাড়ি লাথি দিয়ে, কামড়াতে উদ্যত হলেন।
মেয়েকে কবর দেয়ার পর বাবা সেই কবরের পাশে একটা স্মৃতি ফলক বানালেন। প্রতিদিন সেই ফলকের কাছে গিয়ে বসে থাকেন। এভাবে, পুরো একটা বছর পেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় বছরে তাঁর যাতায়াত অনেকটাই কমে এল। কাজের চাপ আগের চেয়ে বেড়েছে। অবসর সময়ও তেমন একটা পান না। তাছাড়া তিনি এখন বুঝতে পারেন–বয়স হয়েছে, চলাফেরায় আগেকার সেই স্বাচ্ছন্দ্য আর নেই। একটু-একটু করে মেয়ের জন্য দুঃখ কমতে থাকল। মাঝে মধ্যে যখন মনে হয়–আজকাল মেয়ের জন্য তেমন দুঃখ করা হয় না–তখন অবশ্য তিনি নিজের কাছে নিজেই ভীষণ লজ্জায় পরে যান। এমনি করে এক সময় তিনি মেয়ের কথা ভুলেই গেলেন।
এরপর তাদের আরও দুটো কন্যাসন্তান হল। কিন্তু কেউই আগের কন্যার মত হল না। একজন চলে গেলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় অন্য কেউ এসে তা কখনোই পূরণ করতে পারে না।
সংসার এখন একেবারেই রং-রূপহীন, বৈচিত্র্যহীন হয়ে গেছে। স্ত্রীর বয়স হয়েছে। আগেকার সেই সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। স্বামীর আচরণেও বয়সের ছাপ স্পষ্ট। এক সময়ের সোনায়-মোড়ানো সংসার এখন সাদামাটা। ছেলেমেয়েগুলো বেশ চঞ্চল হয়েছে। বাড়িঘরজুড়ে তাদের দুরন্তপনার চিহ্ন ছড়ানো-ছিটানো। বাবা-মায়ের বিয়ের উপহার তো অনেক আগেই ভেঙ্গেচুরে একাকার করেছে, ঘরের আসবাবপত্রও তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি–খাটের তোষক ছেঁড়া, টেবিলের পায়া ভাঙ্গা, সোফার কভারের ফুটো দিয়ে শতচ্ছিন্ন ফোম উঁকি দিচ্ছে, আরও যে কত কি! পিয়ানোটা অনেকদিন মধুর সুরে বাজে না। পরিবর্তে বাচ্চাদের কর্কশ চাচামেচিতে বাড়িঘর ঢেকে থাকে। ‘আদর’, ‘ভালোবাসা’ শব্দগুলো অনেক আগেই পুরনো হয়ে গেছে। ওগুলোকে যেন ময়লা মোছার ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। প্রেমস্পর্শ’ বলতেও কিছু আর নেই এখন। স্পর্শ এখন শুধু প্রয়োজন ফুরানোর প্রচেষ্টা মাত্র। বাবাকে আর মায়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসতে দেখা যায় না। তিনি বসে থাকেন একটা জীর্ণশীর্ণ আর্মচেয়ারে। চুরুট জ্বালানোর দরকার হলে মাকে ডাকেন। এর বাইরে দুজনের তেমন কথাবার্তা হয় না। স্পষ্ট বুড়িয়ে যাচ্ছেন। জীবনের রং ফিকে হয়ে যাচ্ছে।
*** *** ***
বাবার বয়স যখন পঞ্চাশের কাছাকাছি, হঠাৎ করেই তখন মা মারা গেলেন। বাবাকে যেন এবার অতীত এসে জাপটে ধরল। মায়ের হালকা-পাতলা-রুগ্ন। শরীরটা কবরে নামানোর সময় তাঁর চোখে ভেসে উঠল চৌদ্দ বছরের এক কিশোরীর ছবি। অনেকদিন আগে হারানো কিশোরীটির শোকে পাগলপারা হলেন তিনি। সে শোক আজ আফসোস হয়ে ঝরে পড়ছে। বাবা অবশ্য কখনোই মাকে কোন অযত্ন বা অবহেলা করেননি। সেই চৌদ্দ বছরের। কিশোরী, পাদ্রির কন্যাটির প্রতি তিনি সব সময়ই বিশ্বস্ত ছিলেন। সেই কিশোরীকে পূজা করতেন তিনি, হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করতেন। কিন্তু সে প্রার্থনার মন্দিরে প্রবেশ করার সুযোগ পাননি তিনি; কারণ তিনি বিয়ে করেছিলেন চব্বিশ বছর বয়সী এক মলিনকেশী নারীকে। অকপট স্বীকারে মানতেই হত, তিনি ঐ চৌদ্দ বছরের কিশোরীটির জন্যই শোক করছিলেন। তবে একথাও সত্য, বৃদ্ধা স্ত্রীর চমৎকার রান্না আর সীমাহীন যত্নআত্তির প্রচন্ডরকম অভাব বোধ করছিলেন তিনি। যদিও দুটো অনুভূতির মধ্যে বিস্তর ফারাক।
এতদিনে সন্তানদের সঙ্গে বাবার বেশ ভালো বন্ধুত্ব হল। সবাই অবশ্য এখন আর বাড়িতে থাকে না। লেখাপড়া, চাকরীর জন্য কেউ কেউ অন্যত্র থাকে। যারা বাড়িতে থাকে তাদের সঙ্গেই বাবা সারাদিন গল্পগুজব করেন। তবে তিনি সন্তানদের সঙ্গ উপভোগ করলেও সন্তানরা তাঁর সঙ্গ কতটা উপভোগ করে সেটা নিয়ে সংশয় আছে। কারণ সন্তানদের নিয়ে বসলে তিনি একই গল্প বারবার বলেন, স্ত্রীর নানা মজার কাহিনি শোনান। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই দেখা গেল, গল্পগুলো কেমন একঘেয়ে হয়ে গেছে। বাবা। অবশ্য সমান আগ্রহ নিয়েই বলে যান…
*** *** ***
একদিন এক কাকতালীয় ঘটলা ঘটল–বাবার সঙ্গে এক অষ্টাদশী স্বর্ণকেশীর দেখা হল। দেখতে ঠিক সেই কিশোরী প্রিয়ার মত। বাবার কাছে। এ কাকতালীয়তাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে হল। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, ঈশ্বর তাঁর ভালোবাসাকে ফিরিয়ে দিতে চাইছেন। মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেলেন তিনি, বিয়েও করলেন। এতদিনে তিনি যেন সেই কিশোরী প্রিয়াকে আপন করে পেলেন। কিন্তু বিপত্তি বাধলো সন্তানদের। নিয়ে। বিশেষত, তাঁর মেয়েরা এ ঘটনায় ভীষণ ক্ষেপে গেল। তাদের পক্ষে কিছুতেই এটা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। বাবা তাদের মায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলেই ধরে নিল তারা। সুতরাং বাবার সঙ্গে আর থাকা সম্ভব নয়। সন্তানরা যার যার মত নিজের পথ বেছে নিল। তবে বাবা কিন্তু নিজের কাজে যথেষ্ট সন্তুষ্ট। নতুন স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর যতটা না সুখ, তার চেয়ে বেশি গর্ব। বন্ধুদের কাছে স্ত্রীর গল্প করে তিনি বাহ্বা পাওয়ার চেষ্টা করেন। বন্ধুরা অবশ্য ভালোমন্দ কোন মন্তব্য করে না। দু’একজন শুধু বলেছে–“কয়েকটা দিন যেতে দাও, তখন দেখা যাক কী হয়।”
বছর না-ঘুরতেই নতুন স্ত্রী এক সন্তান জন্ম দিল। বাবার অবশ্য এখন আর বাচ্চাকাচ্চার কান্নাকাটি শোনার মত যথেষ্ট ধৈর্য নেই, রাতের বেলার বিশ্রামই বেশি কাক্ষিত। স্ত্রীর ওজর-আপত্তি উপেক্ষা করে তিনি শোবার ঘর আলাদা করার জোর প্রচেষ্টা চালালেন। উপায় না-দেখে স্ত্রী তো কান্নাকাটি করে অস্থির। “উফ! মেয়েরা যে কী পরিমাণ বিরক্তিকর!” যন্ত্রণার এখানেই শেষ নয়। দেখা গেল নতুন স্ত্রী আজকাল প্রথম স্ত্রীকে হিংসা করতে শুরু করেছে। দোষটা অবশ্য স্বামীর অতি সরলভাবে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রথম স্ত্রীর সমস্ত গল্প বলেছিলেন, প্রেমপত্রগুলো পড়তে দিয়েছিলেন এবং, সর্বোপরি, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয় স্ত্রীর অস্বাভাবিক মিলের কথা বলেছিলেন। এত কিছুর জানার পর দ্বিতীয় স্ত্রীর মনে হয়েছে–স্বামী আসলে তাকে ভালোবাসে না; বরং ভালোবাসে তার মধ্যে প্রথম স্ত্রীর ছায়াকে। সে আরও আবিষ্কার করেছে তাকে যেসব আদরের নামে ডাকা হয় সেগুলোর সবই প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল। অর্থাৎ, স্বামী আসলে তাকে অবহেলা করে। এই অবহেলা সহ্য করা সম্ভব নয়। অতএব, সে স্বামীর ভালোবাসা (যেটা শুধুই তার নিজের জন্য) আদায় করতে উঠে-পড়ে লাগল। নানা শয়তানী পরিকল্পনাও করলো। কিন্তু সেগুলোর কোনটাই স্বামীর মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক ভিন্ন কিছু করতে পারল না। ওদিকে স্বামীর মনে দুই স্ত্রীর মধ্যে তুলনা করা শুরু হয়ে গেল। সবদিক বিবেচনায় প্রথম স্ত্রীকেই সেরা বলে মনে হল। সন্তানদের প্রতিও আবার ভালোবাসা জেগে উঠল। ওদের বাড়ি ছেড়ে যেতে দেওয়ায় নিজের প্রতি ভীষণ রাগ হল, অনুশোচনা হল। আজকাল তিনি ঘুমের মধ্যে খারাপ স্বপ্ন দেখে ধড়ফড় করে জেগে উঠেন। মনে হয়, প্রথম স্ত্রীর স্মৃতি যেন তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সর্বোপরি, নিজেকে আজকাল বিশ্বাসভঙ্গকারী মনে হয়।
ঘরে তিনি আর কোনও শান্তি খুঁজে পান না। সবসময় মনে হয়, যেন এমন একটা চুক্তি করেছেন যে-চুক্তির শর্তগুলো পূরণ না-করাটাই শ্রেয়। অতএব ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন তিনি। আজকাল বেশির ভাগ সময় কাটে ক্লাবে-ক্লাবে। স্ত্রীর এ-নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। মাঝে মাঝেই দুজনের মধ্যে ভীষণ কলহ হয়। স্ত্রীর মতে, স্বামী তাকে ধোঁকা দিয়েছে। অমন বুড়ো ভামের ঘরে যুবতী বৌ থাকা ঠিক না। ঘরে যুবতী বৌ রেখে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ালে তার ফল কক্ষনো ভালো হয় না। এজন্য পরে তাঁকে পস্তাতে হবে।
কী! এতবড় কথা! ‘বুড়ো’! স্ত্রী তাকে বুড়ো বলল! সে-ও দেখিয়ে দেবে, সে আসলে বুড়িয়ে যায়নি।
অতএব, দুজনের আবার এক-রুমে থাকা শুরু হল। তবে এবার যেটা ঘটল সেটা আগের চেয়েও শতগুণে খারাপ! বাচ্চার কান্নাকাটি সহ্য হয় না
–স্ত্রীর সাথে রাগারাগি করেন –“বাচ্চারা থাকবে নার্সারিতে, ঘরের মধ্যে এত উৎপাত কিসের?”।
স্ত্রী-ও ঠোঁট উল্টে প্রতিবাদ করে, “কই, আগের বৌয়ের বাচ্চাদের বেলায় তো এমন মনে হয়নি!”
অতএব, স্বামীকে যাবতীয় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হয়…
*** *** ***
এ-পর্যন্ত দু’বার তিনি ফিনিক্স পাখির (রূপকথার পাখি। মৃত পাখির ছাই থেকে নতুন পাখির জন্ম হয়।) জাগরণে বিশ্বাস করেছেন। সে-জাগরণ তাঁর চৌদ্দ-বছরের কিশোরী বধূর জাগরণ। প্রথমবার, তাঁর মৃত কন্যার মধ্যে সেই জাগরণ দেখেছেন; পরেরবার দেখেছেন দ্বিতীয় স্ত্রীর মধ্যে। কিন্তু তাঁর স্মৃতি তাকে কখনোই সেই চৌদ্দ-বছরের কিশোরীটিকে ভুলতে দেয়নি। বুনো স্ট্রবেরিতে রং লাগার সময় পাদ্রির বাড়িতে সেই প্রথম দেখা, প্রথম চুম্বন, প্রথম প্রেমাবেগ সবই যেন স্মৃতিতে অমলিন হয়ে রয়েছে। কিন্তু সেই প্রথম প্রেমকে কখনোই আপন করে পাননি তিনি। এখন জীবনসায়াহ্নে এসে অন্ধকার হাতড়ে বৃদ্ধা স্ত্রীকেই বারেবারে মনে পড়ে, যে তাঁকে আর তাঁর সন্তানদের ভীষণ ভালোবাসত, আদরযত্ন করত; যে কখনোই তাঁর সঙ্গে রাগারাগি করেনি, যে সবসময়ই খুব সাধারণভাবে থাকত, নীরবে বসে স্বামী-সন্তানদের জামাকাপড় সেলাই করে দিত।
এতদিনে নিজেকে জীবনযুদ্ধে পরাজিত বলে মনে হয়। সত্যিকারের ফিনিক্স পাখি তিনি আসলে কখনো চিনতেই পারেননি। হয়ত তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী ই ছিল সত্যিকারের ফিনিক্স পাখি! সেই চৌদ্দ-বছরের কিশোরীর ছাই থেকে জন্ম নিয়ে ধীরে-ধীরে সে পরিণত হয়েছে, ডিম দিয়েছে নতুন ছানা জন্ম দেবার জন্য। তারপর, সে-ডিমে তা দিতে বুকের পালক ছিঁড়ে বাসা বেঁধেছে, ডিমের যত্ন নিয়েছে, ছানাদের বাঁচিয়ে রাখতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে নিজে পুড়ে ছাই হয়েছে। আফসোস! জীবনভর এই ধাঁধার পেছনে ছুটলেন তিনি! কিন্তু ক্লান্ত-শ্রান্ত মাথাটি শেষবারের মত বালিশের ওপর রাখার আগে, এই ভেবে তিনি স্বস্তি নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন শেষ পর্যন্ত ধাঁধাটির সমাধান তিনি করতে পেরেছেন।
বিবাহ অনিবার্য
খুব অল্প বয়সে বাবাকে হারানোর পর মা, দুই বোন, আর খালাদের কাছেই ও মানুষ হয়েছিল। পুরো পরিবারে ছেলে-মানুষ বলতে ও একাই। সুইডেনের এক মফস্বল শহরে ওদের বসবাস। শহরটার নাম সোয়েডারম্যানল্যান্ড। চারপাশে এমন কোন প্রতিবেশী ছিল না যার সঙ্গে বসে প্রাণ খুলে একটু আলাপ করা যায়। সুতরাং, বাড়ির মধ্যেই পুরো পৃথিবী। ওর বয়স যখন সাত, তখন ওদের পড়ানোর জন্য একজন গভর্নেস রাখা হল। কিছুদিন পর এক খালাতো বোনও এসে যোগ দিল, বোনটি এখন থেকে ওদের বাড়িতেই থাকবে।
ও সবসময় বোনদের সাথে সাথেই থাকত। একসঙ্গে খেলা করত, এমনকি গোসলেও যেত। কেউই ওকে ভিন্ন লিঙ্গের কেউ বলে গণ্য করত না। তবে, এই একসঙ্গে থাকায়, কিংবা খেলা করায় সবসময়ই ওকে বোনদের কর্তৃত্ব মেনে চলতে হত, নিজের মতামত প্রকাশ করার কোন সুযোগ ছিল না। ফলে অচিরেই বোনেরা ওর শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হল। অবশ্য, শিক্ষক না বলে প্রভু বলাটাই শ্রেয়তর; কারণ, বোনেরা যেভাবে যা করতে বলত তার বাইরে যাবার কোনও উপায় ছিল না।
ছোটবেলায় ওকে দেখে বেশ শক্ত-পোক্ত একটা ছেলে বলেই মনে হত। কিন্তু এত রমণীর ভিড়ে ধীরে-ধীরে ও কেমন শান্ত, লাজুক প্রকৃতির হতে থাকলো। নিজের জগত্তাকে ঘরের ভেতরেই গুটিয়ে রাখতে শুরু করল। মুক্ত হবার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা অবশ্য একবার ও করেছিল আশেপাশের সমবয়েসী ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিল। সমস্ত দিন জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করেছিল, গাছে চড়েছিল, পাখির বাসা চুরি করেছিল, কাঠবিড়ালি তাড়িয়ে বেড়িয়েছিলো, আরও কত কি! ফ্রিদিওফকে দেখে তখন সদ্যমুক্ত কোন আসামির মত মনে হচ্ছিল–মুক্তির আনন্দ যার পরম আরাধ্য। সেদিন রাতে খাবার জন্য বাড়ি ফেরেনি ও। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে কোথা থেকে গাদাগাদা বুনো জাম জোগাড় করে খেয়েছিল। তারপর লেকের পানিতে দলবেঁধে ঝাপাঝাপি। এটাই ছিল ফ্রিদিওফের জীবনের প্রথম সত্যিকার আনন্দের দিন।
ফ্রিদিওফ যখন বাড়ি ফিরল, তখন সমস্ত বাড়ি কেমন থমথম করছে। মা এতক্ষণ ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন; কিন্তু ফ্রিদিওফ ফেরার পর আর আনন্দ গোপন রাখতে পারলেন না–জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না করে দিলেন। এতকিছুর মধ্যেও একজনের আচরণ সবার থেকে আলাদা দেখালো–ফ্রিদিওফের খালা অগাস্থা। মহিলা বয়সে ওর মায়ের চেয়ে বড় হলেও বিয়ে করেননি বলে এ সংসার মূলত তার কর্তৃত্বেই চলে। ফ্রিদিওফ দেরি করে বাড়ি ফেরায় অগাস্থা ভীষণ রেগে গেল। রীতিমত অগ্নিশর্মা যাকে বলে! তার মনে হল, এই মুহূর্তে ওকে শক্ত শাস্তি না-দেয়াটা একটা অপরাধের সমতূল্য হবে। ফ্রিদিওফ কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, এটা অপরাধ হয় কী করে! কিন্তু অগাস্থাকে বোঝায় কার সাধ্য, অবাধ্যতা তার কাছে পাপের শামিল। অবশ্য, ফ্রিদিওফেরও নিজের পক্ষে যুক্তি ছিল “আমাকেতো কখনো আশেপাশের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে বারণ করা হয়নি।” অগাস্থা এসব কানে তুলতে নারাজ। তার স্পষ্ট ঘোষণা–“এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন কথা শুনতে চাই না।” অতএব, মায়ের ক্ষীণ আপত্তি উপেক্ষা করে, ফ্রিদিওফকে শাস্তি দেবার জন্য জোর করে অগাস্থার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ওর বয়স বড়জোর আট হলেও দেখতে বেশ বড়োসড়ো না দেখায়। অগাস্থার চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ফ্রিদিওফের কপালে । আজ খারাপ কিছু আছে। কিন্তু ঠিক কোন মুহূর্তে যে সেটা ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছিল না। হঠাৎ করেই ফ্রিদিওফের প্যান্ট টেনে খোলার জন্য অগাস্থা ওর কোমরের বেল্ট ধরে ঝাঁকুনি দিল। সাথে সাথে ফ্রিদিওফের সারা শরীর কেমন হিম হয়ে গেল। মনে হলো, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, বুকের ভেতর কে যেন গুমগুম হাতুড়ি পেটাচ্ছে। কিন্তু কোন শব্দ করল না; শুধু ভীতু শালিকছানার মত খালার দিকে চেয়ে রইল। অগাস্থা কিন্তু এতে কোন ভ্রুকুটি করল না। থমথমে গলায় বলল–“চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবি, কোনরকম বজ্জাতি করবি না।” এ-পর্যন্তও মেনে নিয়েছিল ফ্রিদিওফ, কিন্তু খালা যখন শার্টে হাত দিল তখন রাগে-লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে গেল। চট করে লাফ দিয়ে সরে যেতে চাইল। মনে হল, অগাস্থার গা বেয়ে যেন কোন ঘৃণ্য-নোংরা কিছু বেড়িয়ে আসছে। চট করে ফ্রিদিওফের কাছে নিজের লিঙ্গ-পরিচয় আবিষ্কৃত হল। লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করল ও, কিন্তু সফল হল না। অগাস্থা পাগলের মত হিংস্রতায় খপ করে ধরে ফেলল। তারপর, একটা চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে থাকল। সেই মুহূর্তে ফ্রিদিওফের মনে হল, ও যেন কোন ব্যথা অনুভব করছে না; কিন্তু রাগে চিত্তার করতে থাকলো। ক্রমাগত কিল-ঘুষি চালিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল। কিন্তু হঠাৎ করে কী যেন হল–সমস্ত শরীর কেমন নিথর-নিস্তেজ হয়ে এল। অগাস্থা যখন ছেড়ে দিল, তখনও ঠিক অমনই নিথর পড়ে রইল ফ্রিদিওফ।
“উঠে দাঁড়া!” কর্কশ গলার আদেশ শোনা গেল। উঠে দাঁড়াল ফ্রিদিওফ। খালার দিকে নিস্পলক চেয়ে রইল। মহিলার মুখের এক দিক। কেমন ফ্যাকাশে, আর অন্যদিকটা লালচে দেখাচ্ছিল, চোখ দুটো জ্বলছিল, সমস্ত শরীর কেমন থরথর করে কাঁপছিল। এবার আগ্রহ নিয়ে অগাস্থার দিকে তাকালো ফ্রিদিওফ–যেমনভাবে আগ্রহ নিয়ে মানুষ কোন বুনো জন্তুর। দিকে তাকায়। হঠাৎ ওর ঠোঁটে এক ধরনের অবজ্ঞার হাসি খেলে গেল। মনে হল ঘৃণা আর অবজ্ঞার প্রকাশই এই পরিস্থিতিতে ওকে জয়ী করবে। ‘ডাইনি মাগী!’ পাড়ার ছেলেদের থেকে নতুন শেখা গালিটা ভীষণ ঘৃণাভরে অগাস্থার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে, জামা-কাপড় তুলে, দ্রুত পালিয়ে গেল। নীচতলায় বসে ওর মা কাঁদছিল। সেখানে গিয়ে খালার নামে অভিযোগ ঝেড়ে প্রাণ জুড়াতে চাইলে ফ্রিদিওফ; কিন্তু লাভ হলো না। বড় বোনের বিরুদ্ধে ছেলেকে সান্ত্বনা দেবার মত সাহস মায়ের ছিল না। অতএব, ফ্রিদিওফকে সরে পড়তে হল। এলোেমলো হাঁটাহাঁটি করতে করতে রান্নাঘরে চলে এল। এখানে অবশ্য সান্তনা পাওয়া গেল। বাড়ির কাজের লোকেরা ওকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে-শুনিয়ে শেষমেষ কতগুলো খুচরো টাকা হাতে গুঁজে দিল, এতে বেশ কাজ হল।
ঐদিনের পর থেকে বোনদের সাথে নার্সারিতে ঘুমানো বন্ধ হল। মা। নিজের রুমে ফ্রিদিওফের খাট স্থানান্তর করলেন। কিন্তু ওর কাছে মায়ের। রুমটাকে ভীষণ বদ্ধ মনে হল। তাছাড়া, রাত-বিরাতে মা ঘুম থেকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করতেন, ও সেরে উঠেছে কি না। ফ্রিদিওফের এতে বিরক্তির সীমা ছিল না। রাগে গজগজ করতে করতে মায়ের প্রশ্নের জবাব দিত।
*** *** ***
কেউ ঠিকঠাক মত সাজিয়ে-গুছিয়ে না-দেয়া পর্যন্ত বাইরে বেরোনো বারণ ছিল ফ্রিদিওফের। অনেকগুলো মাফলার ছিল ওর। নিজেও জানতো না কখন কোনটা পরতে হবে। কখনও মাফলার না পরে চুপিচুপি বাসা থেকে বেরোতে চেষ্টা করলেই কেউ-না-কেউ জানালা দিয়ে ঠিক দেখে ফেলত। তখন আবার ঘরে এসে মাফলার, ওভারকোট পরে তার পর বের হতে হত।
দিনে দিনে বোনদের খেলাগুলি বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। ওর পেশীবহুল হাত বাচ্চাদের খেলনা র্যাকেট কিংবা শাটলককে আর আনন্দ পেত না। বরং, পাথর ছুঁড়ে খেলা করাকে বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস মনে হত। ঘাসের মাঠে কাঠের বল ছুঁড়ে মারার খেলা নিয়ে প্যানপেনে ঝগড়াও ভীষণ বিশ্রী লাগত–“ধুর! এগুলোয় না লাগে কোন শক্তি, না কোন বুদ্ধি।” ওদিকে, এতসব যন্ত্রণার মাঝে আরেক মহাবিরক্তির কারণ ছিল–ওদের গভর্নের্স। এই মহিলা সব সময় ফ্রেঞ্চ ভাষায় নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত। ফ্রিদিওফ নির্বিকারে সুইডিশে সেসবের জবাব দিত। এভাবে, দিনে দিনে চারপাশের সবকিছু মিলে কেমন একটা গুমোট পরিবেশ সৃষ্টি হতে লাগলো।
ফ্রিদিওফের উপস্থিতিতে সবাই যেভাবে খোলামেলা আলোচনা করত সেগুলো ওর মোটেই পছন্দ হত না। ফলে, মাঝে মাঝেই বাড়ির সবার সঙ্গে। খারাপ ব্যবহার করত। একমাত্র মা-ই ওকে কিছুটা বুঝতে পারতেন। তাই মাঝেমাঝে খানিকটা সময় নিজের মত করে কাটানোর সুযোগ করে দিতেন, ফ্রিদিওফের খাটের চারপাশে তিনি বড় করে পর্দা টানিয়ে দিলেন। এতে লাভ যেটা হলো তা হচ্ছে, বাড়ির সবার সাথে দেখা করাই বন্ধ করে দিল ফ্রিদিওফ। ওদেরকে দেখলেই কেমন গা জ্বালা করে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, শুধুমাত্র রান্নাঘর আর কাজের লোকদের বিশ্রামের। জায়গাগুলোই ফ্রিদিওফের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠলো। এই জায়গাগুলোতে ওর সবরকম আচরণ সহজেই গ্রহণযোগ্য ছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য এমন সব। বিষয় নিয়ে আলোচনা হত যেগুলো যেকোন ছেলের মধ্যেই কৌতূহল জাগাবে; তবে ফ্রিদিওফের জন্য সেসব বিষয়েও কোন রাখঢাক ছিল না। অতএব, সে যখন যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারতো, তা-ই করতে পারতো। একবার তো ভুল করে কাজের মেয়েদের গোসলের জায়গাতেই চলে গেল! এ-দৃশ্য দেখে ওদের গভর্নের্স চিৎকার করে উঠলো। ফ্রিদিওফ অবশ্য কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে যায়নি, তাই গভর্নেসের চিৎকারে কোন আমলই দিল না। বরং, আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা পানিতে ভেসে বেড়ানো মেয়েদের সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে থাকলো। ওদের নগ্নতা ফ্রিদিওফের মধ্যে কোনও ভাবান্তর সৃষ্টি করল না।
এভাবেই ফ্রিদিওফ একসময় তারুণ্যে প্রবেশ করল। ওকে ফার্মের যাবতীয় কাজ শিখিয়ে-পড়িয়ে দেবার জন্য একজন ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হল। কারণ স্পষ্ট: কিছুদিন পর ওকেই তো সব দায়িত্ব নিতে হবে। প্রচলিত। রীতিনীতিতে বিশ্বাস করে এমন একজন বয়স্ক লোককে নিয়োগ দেয়া হল। ভদ্রলোকের সনাতন চিন্তা-ভাবনা কোন যুবককে আলোড়িত করার মত নাহলেও সেগুলো ফ্রিদিওফের মধ্যে বেশ পরিবর্তন আনলো, ওর চিন্তা জগতে কতগুলো নতুন দিক যোগ করলো, আর সর্বোপরি, ওকে কাজেকর্মে বেশ আগ্রহী করে তুললো। কিন্তু জট বাধলো অন্য জায়গায় বাড়ির ভেতর থেকে ভদ্রলোকের জন্য এত বেশি ফরমায়েশ আসে যে, সেগুলো নিয়েই তার সারা দিন কেটে যায়।
*** *** ***
পনেরো বছর বয়সে ফ্রিদিওফকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হল। এ-উপলক্ষে সে একটা স্বর্ণের ঘড়ি উপহার পেল। নিজেকে হঠাৎ বেশ বড় মানুষ মনে হতে লাগলো। এখন সে চাইলেই যখন-তখন ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে যেতে পারে। অবশ্য কিছু বিষয়ে বরাবরের মতই নিষেধাজ্ঞা ছিল, যেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ‘বন্দুক নিয়ে শিকারে যাওয়া, অথচ এটাই ছিল ফ্রিদিওফের সবচেয়ে বড় শখ। যাহোক, আনন্দের ব্যাপার হল, এখন আর খালার হাতে মার খাওয়ার ভয় নেই। খালাকে এতদিন সে ঘোরতর শত্রু বলেই মনে করে এসেছে। তবে, খালার মারের ভয় না-থাকলেও ভয় কিন্তু একটা ছিল ‘মায়ের চোখের জল’। মায়ের কাছে ও সেই শিশু হয়েই রইল। ফলে অন্য মানুষের কথামত নিজের পছন্দ ঠিক করার অভ্যাসটা আর কখনোই পরিবর্তন করতে পারলো না ফ্রিদিওফ।
মাঝে কিছু বছর গেল।
ফ্রিদিওফ এখন বিশ বছরের যুবক। একদিন ও রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কাজকর্ম দেখছিল। একটা মেয়ে পিঁড়িতে বসে মাছ কুটছিল। সদ্যযৌবনা মেয়েটা দেখতে মন্দ নয়। এরই মধ্যে ওর সঙ্গে খানিকটা ভাবও হয়েছে। আজ ফ্রিদিওফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটার সাথে মজা করছিল। এক পর্যায়ে খেলাচ্ছলে মেয়েটাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। মেয়েটা বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল, কোনমতে বলল–“কী করছেন!”
“যা করছি ঠিকই করছি” আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ফ্রিদিওফ।
“কেউ দেখে ফেলতে পারে” ভীত শোনাল মেয়েটাকে।
–দেখলে দেখুক।
রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ফ্রিদিওফের মা হেঁটে যাচ্ছিলেন। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়তেই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্য দিকে হাঁটা দিলেন। এইবেলা ফ্রিদিওফ বেশ অস্বস্তিতে পড়ল। কী করবে ভেবে না পেয়ে, চট করে নিজের রুমে সটকে পড়ল।
*** *** ***
সম্প্রতি বাড়ির বাগানে নতুন মালী রাখা হয়েছে। কাজের মেয়েরা যাতে কোন ঝামেলায় না পড়ে সেজন্য বুদ্ধি করে একজন বিবাহিত লোককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে কোন দিক থেকে আসে তা কি আর কেউ বলতে পারে? নতুন মালীর বিয়ের বয়স অনুযায়ী তার পক্ষে কোন সুন্দরী তরুণীর বাবা হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং, বাগানের সমস্ত গোলাপের মাঝে হঠাৎ করেই একদিন এক ফুটন্ত গোলাপের দেখা পেল ফ্রিদিওফ। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত প্রেমাবেগ পাখনা মেলে দিলো। মেয়েটা যেমন সুশ্রী তেমন শিক্ষিত। প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে গেল ফ্রিদিওফ। ফলে শীঘ্রই ওর জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এল। এখন ওকে যখন-তখন বাগানে দেখা যায়। মেয়েটার সাথে কথা বলার জন্য সবসময়। তক্কেতক্কে থাকে। কিন্তু মেয়েটা তেমন গা করে না। তবে এর ফলাফল হল বিপরীত–মেয়েটার আপাত-অবহেলা ফ্রিদিওফকে আরও বেশি আগ্রহী করে তুললো।
একদিন ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্যে ঘুরছিল ফ্রিদিওফ, মাথায় ঘুরছিল মেয়েটার চিন্তা। ও ধরেই নিয়েছিল, কোন মেয়ে এতটা নিখুঁত কখনো হতে পারে না। মেয়েটার সঙ্গে একাকী দেখা করার ইচ্ছা ওকে পাগল করে তুলছিল। এতে যে কেউ খারাপ ভাবতে পারে তা মাথায়ই ছিল না। চিন্তাভাবনার উন্মত্ততায় এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে, মেয়েটাকে ছাড়া জীবন অসম্ভব ঠেকছিল। হালকাভাবে ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছিল। ফ্রিদিওফ, ফলে ঘোড়াটা ইচ্ছেমত এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করতে পারছিল। হঠাৎ, কোথা থেকে যেন একরাশ আলোর ঝলক খেলে গেল গাছের আড়ালে মালীর মেয়েকে দেখা গেল। ফুটপাথ ধরে হাঁটছিল মেয়েটা; দেখে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল ফ্রিদিওফ। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে, চট করে ঘোড়া থেকে নেমে, মাথার হ্যাট খুলে, মেয়েটার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো। ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরে রেখে এটা-সেটা নানান কথার ছুঁতোয়, ফিসফিস করে নিজের ভালোবাসার কথা জানাতেও ভুল করলো না। অথচ মেয়েটা কিন্তু শুরুতেই হতাশ করল। কষ্টজড়ানো কণ্ঠে। বলল,”এসব চিন্তা অবাস্তব, মিস্টার ফ্রিদিওফ”।
“কোনটা অবাস্তব?” গর্জে উঠলো ফ্রিদিওফ
–আপনার মত একজন ধনী ভদ্রলোক আমার মত গরীব ঘরের একটা মেয়েকে বিয়ে করবে, এই পুরো চিন্তাটাই অবাস্তব।
কেন যেন কথাগুলো মেয়েটার মুখে খুব বাস্তবসম্মত লাগছিল। ফলে, ফ্রিদিওফ একেবারে মুষড়ে পড়ল। ও জানে, মেয়েটার প্রতি ভালোবাসা সত্য। কিন্তু এটাও সত্য যে, এ ভালোবাসাকে সসম্মানে বাড়িতে স্থান, দেয়াটা অনেকটা দিবাস্বপ্নেরই মত। কারণ বাড়িতে নারীকুল যে গুমোট পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে, সেখানে ভালোবাসার কোন স্থান নেই। ওরা কখনোই ভালোবাসার মূল্য বুঝবে না, হয়তো ফ্রিদিওফের ভালবাসাকে ওরা ছিঁড়েখুঁড়েই ফেলবে।
মেয়েটার সাথে কথপোকথনের পর থেকে ফ্রিদিওফ যেন বাকশক্তিহীন হয়ে গেল। প্রচন্ড হতাশা গ্রাস করল ওকে। ওদিকে, শরৎকাল আসতে-না আসতেই বাগানের মালী চাকরি থেকে অব্যাহতি চাইল। কোনওরকম কারণ না জানিয়েই সে ফ্রিদিওফদের এলাকা ছেড়ে চলে গেল। পরবর্তী দু’সপ্তাহ ফ্রিদিওফ কোনভাবেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারল না। জীবনের প্রথম প্রেম, একমাত্র ভালোবাসাকে হারিয়েছে সে। প্রতিজ্ঞা করল, আর কখনোই ভালোবাসায় জড়াবে না।
এভাবেই, ধীরে ধীরে শরঙ্কাল চলে গেল। দরজায় দাঁড়ালো শীত। এবার ক্রিসমাসে এক নতুন প্রতিবেশী পেল ফ্রিদিওফরা। ভদ্রলোক পেশায় একজন চিকিৎসক। তাঁর ছেলেমেয়েরা বেশ বড় বড়। ফ্রিদিওফের বাড়ির মহিলারা যেহেতু সারাবছরই অসুস্থ থাকেন, দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব জমতে সময় নিল না। বলে রাখা ভালো, ভদ্রলোকের সন্তানদের মধ্যে এক সদ্যযৌবনা কন্যাও ছিল। অচিরেই ফ্রিদিওফ তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করল। শুরুতে সে খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল–মনে হচ্ছিল, এটা তার প্রথম প্রেমের সঙ্গে স্পষ্ট প্রতারণা। কিন্তু সময়ে সে এক ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছল। তার মনে হল, ভালোবাসা বিষয়টা আসলে নৈর্ব্যক্তিক; পরিবেশ পরিস্থিতির বিবেচনায় কারও পছন্দ বদলে যেতেই পারে। সময়ের সাথে সাথে কর্তৃত্ব যেমন স্থানান্তরিত হয়, ভালোবাসার ব্যাপারটাও ঠিক তেমন।
ফ্রিদিওফের বাড়িতে খবর চাউর হতে সময় লাগল না। এ-ব্যাপারে কথা বলার জন্য মা ওকে একদিন ডেকে পাঠালেন। বেশ নাটকীয়ভাবে শুরু করলেন তিনি, “ফ্রিদি, আমার মনে হয় তোমার এখন জীবনসঙ্গী খোঁজার মত বয়স হয়েছে মায়ের গলা থমথমে শোনাল।
“এসব নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, মা! আমি একজনকে পছন্দ করে রেখেছি” ফ্রিদিওফ যেন ঝলমল করে উঠল।
মা এবারে আরও গম্ভীর। মনে হল, যেন খাদের কিনারা থেকে কথা বলছেন তিনি,
–আমার মনে হয়, তুমি একটু বেশিই তাড়াহুড়ো করে ফেলছ। যে মেয়েটাকে তুমি পছন্দ করেছ বলে সন্দেহ হচ্ছে, তার নৈতিকতা-বোধ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। কোন শিক্ষিত মানুষের নৈতিকতা কিছুতেই এমন হতে পারে না।
–কী বলছেন আপনি? অ্যামির নৈতিকতা নিয়ে সংশয়! কে বলেছে আপনাকে এসব?
–এসব কথা শুধু মেয়েটার জন্য বলছি না, বলছি ওর বাবার জন্যও। তুমি বোধহয় জানো না, ওর বাবা একজন নাস্তিক।
-”আস্তিক-নাস্তিক জানি না, কিন্তু জাগতিক মোহকে পাশ কাটিয়ে, খোলা মনে চিন্তা করতে পারেন, এমন মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি।” বেশ দৃঢ়ভাবে কথাগুলো বলল ফ্রিদিওফ।
–ঠিক আছে, এসব না-হয় বাদ দিলাম। কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছ, অন্য জায়গায় তোমার বিয়ে ঠিক করা আছে?
–“মানে কী?” আকাশ থেকে পড়ল ফ্রিদিওফ। “আপনি কি…?”
–হ্যাঁ, লুসিয়ার কথাই বলছি। লুসিয়াও মনে মনে তোমাকে পছন্দ করে।–আমাদের খালাতো বোন লুসিয়া!
মায়ের মুখে হাসি ফুটলো–“তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, ছোটবেলায় তোমরা যখন একসঙ্গে খেলা করতে, তখন একে-অন্যকে বাগদত্তা বলে ভাবতে?”
–কক্ষনো না! আমি কক্ষনো এসব ভাবিনি; বরং, আপনারাই আমাদেরকে এক সাথে খেলতে পাঠিয়েছেন, আর মনে মনে এসব চিন্তা করেছেন।
হঠাৎ করেই মায়ের সুর বদলে গেল, গলায় মিনতি ঝরে পড়ল। “তোমার বুড়ি মা আর বোনদের কথা একবার ভাবো, ফ্রিদি! আমরা সবাই মিলে এতদিন ধরে একটু-একটু করে নিজেদের মত যে পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছি, তার মধ্যে তুমি অপরিচিত কাউকে আনতে চাও? হঠাৎ করে বাইরে থেকে কেউ এসে আমাদের ওপর খবরদারি করলে সেটা মানতে পারবে?
–ও আচ্ছা! আপনারা তাহলে সব দিক চিন্তা করেই লুসিয়াকে বাড়ির কত্রী বানাতে চাইছেন!
–না! কাউকে বাড়ির কত্রী বানাতে চাইছি না। তবে, ছেলের ভবিষ্যৎ স্ত্রী পছন্দ করার অধিকার একজন মায়ের অবশ্যই আছে। আর, এক্ষেত্রে লুসিয়া ছাড়া অন্য কাউকে আমার অতটা উপযুক্ত মনে হয় না। আমার পছন্দে তোমার ভরসা নেই, ফ্রিদি? তোমার কি কখনো মনে হয়েছে, মা তোমার খারাপের জন্য কিছু করবে?
–ভালো-খারাপের কথা এটা নয়। আমি আসলে বলতে চাইছি, ছোটবেলা থেকেই লুসিয়াকে নিজের বোনের মত দেখে আসছি। ওকে আমি কখনোই অন্য দৃষ্টিতে দেখতে পারবো না, ভালোবাসতে পারবো না।
–ভালোবাসা? ভালোবাসার মত অনিশ্চিত জিনিস জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই, মুহূর্তের বাতাসেই এটি উবে যায়। তাই ভালোবাসার ওপর। আস্থা রাখা নিতান্ত বোকামি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, ধর্মীয় আচরণ, সমমানসিকতা আর দীর্ঘদিনের পরিচয়, এই ব্যাপারগুলো একটা সুখী দাম্পত্য জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। এর সবগুলো গুণ লুসিয়ার মধ্যে আছে। ও তোমার জীবনকে ভরিয়ে তুলবে। তুমি যেভাবে চাইবে ওকে নিয়ে সেভাবেই জীবন গড়ে তুলতে পারবে।
ফ্রিদিওফের সামনে একটাই পথ খোলা ছিল–মায়ের কাছে সময় চেয়ে নেয়া। অগত্যা, সে তা-ই করল। চিন্তা-ভাবনার কথা বলে মায়ের থেকে কিছুদিন সময় চেয়ে নিল। ইতোমধ্যে, বাড়ির সবাই যেন রাতারাতি সুস্থ হয়ে উঠল! ফলে, ডাক্তার ভদ্রলোকের এ-বাড়িতে আসা বন্ধ হল। তবুও, হঠাৎ কেন যেন তাঁকে একদিন ডাকা হল। আসার পর ভদ্রলোক বেশ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়লেন–সবার ব্যবহারে স্পষ্ট অবজ্ঞা। মানুষ। হিসেবে তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণ–মূল ঘটনা বুঝতে তাঁর মোটেও সময় লাগল না। তাই কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেলেন। পেছন থেকে ফ্রিদিওফ ডাকলেও, না-শোনার ভান করলেন। এভাবেই, দুই পরিবারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ইতি ঘটলো।
ফ্রিদিওফ কেমন ঝিমিয়ে পড়ল।
ওদিকে, নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে বাড়ির ভেতর নানা অদ্ভুত কর্মকাণ্ড শুরু হল। ফ্রিদিওফের ওপর খালাদের ভালোবাসা ঝরে পড়তে শুরু করল। এমনভাবে তারা যত্নআত্তি শুরু করল যেন ফ্রিদিওফ নিতান্ত নাদান শিশু, আর তাদের দেখভাল ছাড়া ওর পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়! বোনদের আচরণেও লক্ষণীয় পরিবর্তন–তারাও বেশি বেশি যত্নআত্তি করার জন্য একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল! আর, এতকিছুর সমানতালে লুইসারও নিজের পোশাকআশাকের প্রতি সচেতনতা বাড়তে থাকল। সে এখন বেশ আটোসাটো জামা পড়ে, বেণি করে চুল বাঁধে। সুন্দরীতে তাকে কোনওমতেই বলা যায় না; তবে তার চোখ দুটো বেশ শান্ত, সে কথা সত্য। তার চেয়েও বড় সত্য হচ্ছে–তার বাকপটুতা!
ফ্রিদিওফ আগের মতই উদাস হয়ে রইল। যতদিন লুইসার ব্যাপারে কোন চিন্তা ছিল না, ততদিন সে কখনোই লুইসাকে একজন পুরুষ মানুষের দৃষ্টি দিয়ে দেখেনি। কিন্তু ঐদিন মায়ের সাথে কথা বলার পর থেকে লুইসাকে দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে; বিশেষ করে, যখন মনে হয় লুইসা যেন গায়ে পরে ভাব জমানোর চেষ্টা করছে। ফ্রিদিওফ যেখানেই যায় সেখানেই লুইসার সঙ্গে দেখা হয়–সিঁড়িকোঠায়, বাগানে, এমনকি ঘোড়ার আস্তাবলেও! একদিনতো সকালবেলা ওর রুমের মধ্যেই এসে হাজির। ফ্রিদিওফ তখনও বিছানা ছাড়েনি। লুইসা এসে এমন ভাব করল যেন তার মোটেই আসার ইচ্ছা ছিল না। লাজুক-লাজুক ভাব দেখিয়ে ফ্রিদিওফের কাছে একটা সেফটিপিন চাইল! ফ্রিদিওফ শুরুতে বুঝতেই পারলো না ঘটনা কী। চোখ রগড়ে নিয়ে দেখল লুইসা একটা ড্রেসিং জ্যাকেট পরে সামনে দাঁড়িয়ে আছে! দেখে রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলেও সেটা প্রকাশ না করে, কেবল মুখ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক আওয়াজ করলো। এ-জাতীয় নানা কারণে লুইসার প্রতি একরকম বিতৃষ্ণা অনুভব করছিল ফ্রিদিওফ; কিন্তু ওকে মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতেও পারছিল না। ওদিকে, মা ছেলের মধ্যে একের-পর-এক বৈঠক চলছিলো। সাথে খালা আর বোনদের নানা উৎসাহ-উদ্দীপনাতো আছেই। সব মিলিয়ে ফ্রিদিওফের জীবনটা যেন মস্ত এক বোঝায় পরিণত হল, যেন চারদিক থেকে একটা জালে আটকা পড়ে গেছে। এ জাল ছিন্ন করে বেরোবার পথ তার জানা নেই। লুইসাকে এখন বোন বা বান্ধবী কোনটাই মনে হয় না, আবার ভিন্ন কিছুও মনে করতে পারে না। তবে সারাক্ষণ ওর সাথে বিয়ের কথা শুনতে শুনতে এতদিনে মনে হয়েছে–“হ্যাঁ, লুইসা একজন নারী। যদিও এক অসহ্য নারী, তবু সত্যি কথাটা হচ্ছে, সে নারী। হয়তো ওর সাথে বিয়ে হলে হতেও পারে। যদি সত্যিই হয়, তবে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন হবে। হয়তো নতুন সম্পর্কটা হবে আবেগ-অনুভূতিহীন শুধুই একটা বন্ধনের মত।” এসব নানা চিন্তায় বুঁদ হয়ে রইল ফ্রিদিওফ। বাড়ির আশেপাশে আপাতত কোন তন্বী-তনয়া ছিল না। অতএব, ওর চিন্তাগুলো বুদবুদের মত উড়ে যেতেও খুব বেশি সময় লাগলো না–“লুইসাও হয়ত আর দশটা মেয়ের মতই হবে।” এবারে ফ্রিদিওফই আগে মায়ের কাছে গেল–“বিয়ে আমি করতে পারি, তবে শর্তসাপেক্ষে: বাড়ির একাংশের পুরো কর্তৃত্ব আমার হাতে থাকবে, আমি যেভাবে চাইব সেভাবেই চলবে; আর আমার ব্যক্তিগত জিনিসপত্রে কেউ হাত দিতে পারবে না।” এরপর ফ্রিদিওফকে কিছুটা নির্ভার মনে হল। ফিরে আসার সময় আরও জানালো, বিয়ে নিয়ে আর কোন কথাই সে বলবে না, মাকেই পরবর্তী সকল পদক্ষেপ নিতে হবে।
ফ্রিদিওফের শর্তাবলী সানন্দে গৃহীত হল। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হতেও দেরি হল না।
লুইসাকে ডেকে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানানো হল। সেসময় ফ্রিদিওফও সেখানে উপস্থিত ছিল। হঠাৎ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ওরা দুজনেই কেন যেন কান্না করে দিল! আবার যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমন হঠাৎ করেই কান্নাকাটি থেমেও গেল। এ-নিয়ে দুজনে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। সারাদিন আর কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারল না। সবকিছু স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুটা সময় নিল। ওদিকে খালা-বোনদের দরদ দিন দিন উথলে পড়ছে। কী ছেড়ে কী করবে তার কোন হিসেব নেই। বাড়ির দরজা-জানালায় নতুন রং পড়ল, ঘরদোর গোছগাছ হল, আরও কত কি! আর, এ সব হল ফ্রিদিওফের সঙ্গে ন্যূনতম আলোচনা বা পরামর্শ ছাড়াই।
বিয়ের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন। যেখানে যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আছেন সবাইকে দাওয়াত করা হল এবং…
এবং বিয়ে সম্পন্ন হল।
*** *** ***
বিয়ের প্রথম সকালে খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠল ফ্রিদিওফ। বিছানা বালিশ ছেড়ে যত দ্রুত সম্ভব বাইরে বের হল। এমন একটা ভাব যেন বাইরে ভীষণ জরুরি কোন কাজ পড়ে আছে। লুইসা তখনও ঘুম থেকে না
উঠলেও সঙ্গোপনে সব কিছুই লক্ষ্য করছিল। ফ্রিদিওফের ঠিক বেরোবার মুখে পেছন থেকে বলে উঠল
“১১টায় ব্রেকফাস্টের কথা ভুলো না কিন্তু।” কথাগুলো অনেকটা আদেশের মত শোনালো।
শোনার ভান করে নিজের পড়ার রুমে গেল ফ্রিদিওফ। শু্যটিং স্যুট আর ওয়াটারপ্রুফ জুতা পরল। তারপর, খুব সাবধানে ওয়্যারড্রোব থেকে নিজের বন্দুকটা বের করে নিল–এ জিনিসটার কথা এতদিন সে গোপনই রেখেছে। সবকিছু বেশ গুছিয়ে নিয়ে বনের পথে হাঁটা ধরলো।
সময়টা অক্টোবর মাস। চারপাশ সাদা বরফে ঢাকা পড়েছে। ফ্রিদিওফ বেশ দ্রুত হাঁটছে। দেখে মনে হচ্ছে, যেন কোন পিছুটান এড়িয়ে পালাতে চাইছে। তবে সকালের নির্মল বাতাস কিছুক্ষণ পর ওর মনোভাবে পরিবর্তন আনল। ধীরে ধীরে নিজেকে ফিরে পেতে শুরু করল ফ্রিদিওফ। বেশ তরতাজা লাগছে এখন। নিজেকে একজন পূর্ণ-স্বাধীন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। কারণ এই প্রথম তার আজন্ম লালিত স্বপ্ন–বন্দুক নিয়ে বাইরে। যাওয়া–সত্যি হল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এই আপাত-স্বাধীনতার ভাব ফিকে হয়ে এল। এতদিন পর্যন্ত অন্তত একান্ত ব্যক্তিগত একটা শোবার ঘর ছিল, দিনের বেলা ওখানে বসে চিন্তা-ভাবনা করা যেত, রাতের বেলা সেখানে স্বপ্নেরা হানা দিত। এখন যে সেটুকুও অবশিষ্ট রইল না! আরেকজনেরর সঙ্গে শোবার ঘর ভাগ করে নেয়ার চিন্তাটা খুব বাজে লাগে। পুরো ব্যাপারটাকে কেমন একটা নোংরামি বলে মনে হয়। মানব চরিত্রের। বুনো বৈশিষ্ট্যটাকে এভাবে উন্মুক্ত করে দেয়ার কথা কখনো কল্পনাও করেনি ফ্রিদিওফ। কারণ ও বেড়ে উঠেছে অনেকগুলো আদর্শকে সামনে রেখে। নিজের পরিবারের ভেতর এমনটা কখনো হতে দেখেনি। সত্যি কথা বলতে কী, সংসার জিনিসটা ও কখনো কাছ থেকে দেখেইনি। তাই, একজন পুরুষ এবং একজন নারীর একসঙ্গে থাকার চিন্তাটা ওর কাছে নৈতিকতার স্পষ্ট স্থলন বলে মনে হয়। এ যেন লজ্জা-শরমের আবরণকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা, সমস্ত পেলবতাকে ছুঁড়ে ফেলা, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে ধ্বংস করা। এমনকি বিয়ে করা সত্ত্বেও, নারী-পুরুষের মিলনকে সে কিছুতেই মন থেকে মেনে। নিতে পারছে না। এ-তো মিলন নয়, এ-তো দুটো মানুষের মধ্যে নিছক নোংরামি! ফ্রিদিওফের মনে হল, এই জংলি ব্যাপারটার ভয় থেকেই হয়ত ‘নারীত্ব’ চিন্তাটার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে কি এ কথা খাটে? যদি ডাক্তারের মেয়ে কিংবা সেই মালির মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হত, তাহলে কি সেখানে ভয় বলে কিছু থাকত? বরং, একাকী তাকে কাছে পাওয়াটাকে এক ধরনের আশীর্বাদ বলে মনে হত। তখন তাদের মিলন শুধু ‘জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম না হয়ে, আত্মিক বোঝাপড়ার আনন্দে উদ্বেলিত হতে পারত। আফসোস! লুইসার সঙ্গে এগুলোর কোনটাই সম্ভব নয়। এমনকি, ওর সঙ্গে একা দেখা করার চিন্তাটার মধ্যেও কেমন বিশ্রী একটা নিরাসক্ততা আছে।
এ-জাতীয় এলোমেলো চিন্তা করতে করতে বনের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াতে লাগত ফ্রিদিওফ। কী শিকার করবে, কীভাবে শিকার করবে, কোন কিছুই মাথায় এল না। শুধু মনে হচ্ছিল–একটা গুলির আওয়াজ হবে, আর কিছু একটা মারা পড়বে। কিন্তু, মরার জন্য কোন কিছুই বন্দুকের সামনে এল না। মনে হচ্ছে, যেন হঠাৎ করে কোন কারণ ছাড়াই পুরো বনটা পাখিশূন্য হয়ে গেছে, অন্য কোন জন্তু-জানোয়ারও নেই। সহসা একটা কাঠবিড়ালী চোখে পড়ল। সুড়সুড় করে পাইনগাছে উঠছিল, এক ফাঁকে ফ্রিদিওফের দিকে চকচকে চোখে চেয়ে, আবার সুরুৎ করে ছোট্ট লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার চেপে দিল ফ্রিদিওফ–ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কাঠবিড়ালীটা এর মধ্যেই অন্যপাশে চলে গেছে। ফলে, গুলিটা গিয়ে গাছের গায়ে বিধে রইল। একটা লাভ অবশ্য হল–গুলির আওয়াজের পর কিছুক্ষণের জন্য চারপাশে এক ধরনের নিস্তব্ধতা তৈরি হল, পুরো বন যেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রিদিওফ খুব উপভোগ করলো ব্যাপারটাকে, লম্বা করে শ্বাস নিলো। তারপর, হাঁটাপথ ছেড়ে হনহন করে বনের আরও গহীনে পা বাড়ালো। পথিমধ্যে যত ছত্রাক, ব্যাঙের ছাতা বা ছোটখাটো গাছপালা পড়ল সব দুমড়ে-মুচড়ে একাকার করে ফেললো। ফ্রিদিওফের ওপর যেন কিছু ভর করেছে আজ! সবকিছু ধ্বংস করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কোন সাপ কী এ-জাতীয় কিছু যদি চোখে পড়ে, তাহলে পায়ের তলায় খুব করে পিষে মারবে ওটাকে; না-হলে গুলি করে শেষ করে দেবে, তাতে যদি গায়ের জ্বালা জুড়ায়!
হঠাৎ করেই সম্বিত ফিরে পেল ফ্রিদিওফ–বাড়ি ফিরতে হবে, আজ তার বিয়ের প্রথম সকাল। কিন্তু বাড়ি ফিরলে সবাই যে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করবে, সেটা মনে করেই নিজেকে অপরাধী মনে হল। যেন সভ্যতার বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে, ঘোরর কোন অন্যায় করে ফেলেছে। “ইস! এই পৃথিবী ছেড়েছুঁড়ে যদি ভিন্ন কোথাও চলে যাওয়া যেত! কিন্তু সেটাই বা কীভাবে সম্ভব?” এই জাতীয় নানা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে-খেতে ক্লান্ত করে তুলল ফ্রিদিওফকে। কিছুক্ষণ পর ভীষণ ক্ষুধা অনুভব করলো–“নাহ্! বাড়ি ফিরতে হবে, ব্রেকফাস্ট করতে হবে।”
বাড়ির গেটে এসে হতভম্ব হয়ে গেল ফ্রিদিওফ। মনে হল, যেন ওকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গোটা বাড়ির অতিথিরা গেটে এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখামাত্র সবাই চিৎকার করে উঠল। এলোমেলো পা ফেলে বাড়ির দুয়ার পার হলো ফ্রিদিওফ। এদিক-ওদিক থেকে নানাজন, নানাভাবে, ‘শরীর কেমন আছে?’ জিজ্ঞেস করে হাসি-ঠাট্টা করছিল। কিন্তু ফ্রিদিওফ এসবের কোন কিছুতেই কান না-দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। লক্ষ্যই করল না, সবার মাঝে ওর স্ত্রী-ও ছিল। হয়তো আশা করেছিল, ফ্রিদিওফ এসে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করবে!
খাবার টেবিলে বহুমুখি যন্ত্রণা সহ্য করতে হল। এ-এমনই যন্ত্রণা, মনে হল যেন অনন্তকাল দগ্ধ হতে হবে। অতিথিদের চটুল কথাবার্তা, আর ‘বিজ্ঞ পরামর্শে গা জ্বলতে থাকল। এর মধ্যে আবার যোগ হল লুইসার গায়েপরা ন্যাকামি! সবমিলিয়ে, যে-দিনটা জীবনের সবচেয়ে আনন্দের হতে পারতো, সেটাই আজ ফ্রিদিওফের জন্য সবচেয়ে জঘন্য দিনে পরিণত হল।
*** *** ***
কয়েক মাসের মধ্যেই নববধূ বাড়িতে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলল। এ ব্যাপারে ফ্রিদিওফের খালা আর বোনেরা হল তার বিশ্বস্ত সহযোগী। ফলে ফ্রিদিওফ বরাবরের মতই বাড়ির সবচেয়ে নিগৃহীত সদস্য হয়ে রইল। কালেভদ্রে অবশ্য, এটা-ওটা নিয়ে ওর পরামর্শ চাওয়া হত, কিন্তু সে পর্যন্তই পরামর্শের বাস্তবায়ন হত না কখনোই। এমন আচরণ করা হত যেন ও এখনও সেই শিশুটিই আছে!
ফ্রিদিওফের সঙ্গে একা বসে খাওয়াটা কিছুদিনের মধ্যেই লুইসার কাছে অসম্ভব বলে মনে হতে লাগলো। কারণ খাবার টেবিলে ফ্রিদিওফ ইচ্ছে করেই ভীষণরকম নীরব থাকত। এরকমটি সহ্য করা লুইসার পক্ষে সম্ভব ছিল না। খাবার টেবিলে নানারকম গপ্পো করার অভ্যাস ছিল তার। অতএব, অচিরেই খাবার টেবিলে ফ্রিদিওফের বোনদের একজন এসে জুটলো। এহেন নানাবিধ যন্ত্রণায় জীবনটা কেমন বদ্ধ হয়ে গেল। একাধিকবার নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেও প্রতিপক্ষের সামর্থ্যের বিপরীতে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। প্রতিপক্ষ সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়ায় এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। ওরা এমনভাবে খোঁচা দিয়ে কথা বলত যে, অস্থির হয়ে ফ্রিদিওফকে বনে পালিয়ে বাঁচতে হত।
রাত্রিগুলো ছিল সাক্ষাত আতঙ্ক! শোবার-ঘর জায়গাটাকে রীতিমত ঘৃণা করত ফ্রিদিওফ। ওটাকে মনে হত যেন ফাঁসির মঞ্চ! ধীরে-ধীরে ও আরও বেশি খিটখিটে হতে থাকল। আশেপাশের সবাইকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল।
বিয়ের এক বছর পার হল। তখনও সন্তান হবার কোন লক্ষণ নেই মায়ের কপালে কিঞ্চিৎ ভাঁজ। একদিন ফ্রিদিওফকে এককোনে ডেকে নিলেন তিনি,
–“তোমার কি ছেলের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না?” মায়ের গলাটা মিনমিনে শোনালো।
–“অবশ্যই করে” ফ্রিদিওফের জোরালো জবাব।
–“কিন্তু… কিন্তু তুমি বোধহয় তোমার স্ত্রীর সঙ্গে খুব-একটা ভালো ব্যবহার করছ না।” যতটা সম্ভব অস্বস্তি এড়িয়ে, আলগোছে কথাগুলো বলে ফেললেন মা।
এবারে ফেটে পড়ল ফ্রিদিওফ।
–“কী বলতে চান আপনি? আমার দোষ? আপনি কি চান আমি সারাদিন এসব নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করি! লুইসাকে চেনেন না আপনি? ওর স্বভাব জানেন না? এগুলো কি শুধু আমার একার দায়িত্ব? আপনি এমন পক্ষপাতিত্ব করলে আমার পক্ষে কোন জবাব দেয়া সম্ভব না!”
কথাগুলো মায়ের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে বাইরে চলে গেল ফ্রিদিওফ। তবে মা কিন্তু সময় পেলেই ওই একই অভিযোগ করেন।
ধীরে-ধীরে ফ্রিদিওফ আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়ল, ভীষণ একাকীত্ব গ্রাস করল। শেষমেষ, বন্ধুত্ব পাতাললা বাড়ির কেয়ারটেকারের সাথে। কেয়ারটেকার লোকটা বয়সে তরুণ। মদ আর জুয়ায় দারুণ আসক্তি। অভ্যাসগুলো রপ্ত করতে ফ্রিদিওফেরও সময় লাগলো না। ফলে কেয়ারটেকারের রুমেই আজকাল বেশিরভাগ সময় কাটে। রাতে ঘরে ফেরে অনেক দেরি করে। এভাবেই দিন ফুরায়।
এক রাতে বাড়ি ফিরে দেখলো স্ত্রী তখনও জেগে আছে–ওর জন্য অপেক্ষা করছে।
–“কোথায় গিয়েছিলে?” কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল স্ত্রী।
–“সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার।” স্ত্রীর প্রশ্নটা উড়িয়ে দিল ফ্রিদিওফ। স্ত্রীও দমে যাওয়ার পাত্রী নয়,
–বিয়ের পর স্বামী না-থাকাটা খারাপ না! অন্তত, একটা সন্তান যদি থাকত!
–সেটা কি আমার দোষ?
–নয়তো কি আমার?
কার দোষ আর কার নয়, তা নিয়েই এক তুলকালাম কাণ্ড বাঁধলো। শুরু হলো বাকবিতণ্ডা, কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতে রাজি নয়! যেহেতু দুজনেই ভীষণ একগুঁয়ে, কেউই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গেল না। অতএব, যা হবার তা-ই হলো, বিবিধ মতের বিবিধ কানাঘুষা! স্বামীকে নিয়ে মানুষজন চটুল রসিকতা করে, আর স্ত্রীকে সহ্য করতে হয় অসহ্য গঞ্জনা। আশেপাশের মহিলারা স্বামীর কানে বিষ ঢালে, টিপ্পনী কাটে
“বাজা মেয়েদেরকে আসলে ভক্তিই করা উচিত! ঈশ্বরের অভিশাপগুলো সব ওরা নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নেয় যে!”
এই মহিলারা কখনো চিন্তাও করত না, ঈশ্বরের অভিশাপ পুরুষের ঘাড়েও পড়তে পারে।
তবে ফ্রিদিওফের কোন সন্দেহ ছিল না, ঈশ্বরের অভিশাপ ওর ঘাড়েই পড়েছে। না-হলে জীবনটা কখনো এত বিবর্ণ, এত নিরানন্দ হতে পারে না। প্রকৃতি দুটি ভিন্ন লিঙ্গের মানুষ তৈরি করেছে–পুরুষ আর নারী। এ ভিন্ন লিঙ্গের মানুষদের মাঝে কেউ কখনো শত্রু, কখনোবা বন্ধুর দেখা পায়। নিজেকে অভিশপ্ত এ-কারণেই মনে হয় যে, সে দেখা পেয়েছে শত্রুর এক ভীষণ শত্রু, যাকে কোনভাবেই সহ্য করা যায় না।
*** *** ***
একদিনের ছোট্ট একটা ঘটনা ফ্রিদিওফের শেষ শক্তিটুকুও কেড়ে নিল। বোনদের একজনের সামনে দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ করে বোনটি জিজ্ঞেস করে উঠল,
–আচ্ছা, ‘খোঁজা’ কাকে বলে?
বোনটি আপনমনে সেলাই করছিল। বিশেষ কিছু বোঝানোর জন্য সে প্রশ্নটা করেনি। ফ্রিদিওফ প্রথমে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেও পরক্ষণেই সান্তনা নিলো–“ও হয়ত আসলেই শব্দটার অর্থ জানে না! হয়ত কোথাও কারোও মুখে শুনে প্রশ্ন জেগেছে, তাই জিজ্ঞাসা করেছে।” তবুও বুকের ভেতর কোথায় যেন চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করলো ফ্রিদিওফ। উত্তর পেতে দেরি হওয়ায় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল বোনটি। এবার সন্দেহের তীর এসে গায়ে বিধল। মনে হল, চারপাশের সবাই যেন আড়াল থেকে ওকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। কোনদিকে না-তাকিয়ে হনহন করে বাইরে চলে গেল ফ্রিদিওফ। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে, রাগের মাথায়, কাজের মেয়েদের একজনকে ধর্ষণ করে বসল। ফলাফল পেতেও দেরি হল না। যথাসময়ে সন্তানের আগমন ঘটলো।
এবার, মানুষের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর অবস্থান উল্টে গেল। লুইসার প্রতি সবার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল, যেন সে বিশাল কোন আত্মত্যাগ করে ফেলেছে, আর ফ্রিদিওফ হলো ‘কুলাঙ্গার’, ‘দুশ্চরিত্র। কিন্তু এসবের কোনকিছুই ওকে স্পর্শ করল না। ও বরং মনে মনে ব্যাপারটার একটা যুতসই ব্যাখ্যা দাঁড় করালো–“এ ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে, সন্তান না-হবার দোষটা আসলে তার নয়, সে নিখুঁত। আর, নিখুঁত হয়ে জন্মানোটা শুধু সৌভাগ্যেরই নয়, বিরাট সম্মানেরও ব্যাপার। তবে পুরো ব্যাপারটা লুইসার মধ্যে কেমন একটা ঈর্ষার ভাব জন্ম দিল। তার চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, ঈর্ষাটা কীভাবে যেন ‘পতিভক্তি’র রূপ নিল। কিন্তু এ জাতীয় ভক্তি-ভালোবাসায় ফ্রিদিওফ আগের চেয়ে বরং বেশি বিরক্ত হলো। অবিরাম নজরদারি আর ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনধিকারচর্চা কারোরই ভালো লাগার কথা নয়। মাঝে মাঝে এমনকি ভীষণ ছোটখাটো বিষয় নিয়েও লুইসা এমন ব্যাকুলতা দেখাতো যে, ফ্রিদিওফ মেজাজ খারাপ না-করে পারত না–“বন্দুকটা ভুলে লোড করা নেইতো?” কিংবা বাইরে যাবার সময়, “ওভারকোট পরেছেতো?” দৈনন্দিন বিষয় নিয়ে এ-জাতীয় বাড়াবাড়ি মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না ফ্রিদিওফের। ওর ঘরের প্রতিটি জিনিস ভীষণ পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা হত। সেই সাথে সারাদিনজুড়ে থোয়ামোছা তো আছেই! প্রতি শনিবার ঘরের সব জিনিসপত্র বাইরে বের করে কার্পেট পরিস্কার করা হত, কাপড়চোপড় রোদে দেয়া হত। এ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের যন্ত্রণায় ঘরে থাকার শান্তিটুকুও উধাও হল।
সারাদিনে করার মত তেমন কোন কাজ ছিল না ফ্রিদিওফের। কাজের লোকেরাই সব করে দিত। মাঝে কিছুদিন চাষবাস নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখল ওতে আরও উন্নতি করা যায় কি না। কিন্তু কয়েক দিন পরই হাল। ছেড়ে দিলো–যে মানুষ নিজের ঘরের উন্নয়ন করতে পারে না, সে বাইরের উন্নয়ন কী করবে?
একসময় পুরোপুরি হতোদ্যম হয়ে গেল ফ্রিদিওফ। কথাবার্তা বলা প্রায় ছেড়েই দিল; কারণ সে যা-ই বলার চেষ্টা করে তার-ই বিরোধিতা করা হয়। মনের মত কোনও বন্ধু-বান্ধবও নেই যার কাছে একটু হালকা হওয়া যায়। মাথার ভেতরটা সারাক্ষণ কেমন অসার হয়ে থাকে। আবেগ-অনুভূতিগুলোও আজকাল আর আগের মত কাজ করে না–কোনকিছুর প্রতিই কোন টান। অনুভব করে না। সব কিছু ভুলে শেষমেষ মদের নেশায় আসক্ত হলো ফ্রিদিওফ।
*** *** ***
ফ্রিদিওফ এখন বলতে গেলে বাড়িতেই ফেরে না। হরহামেশা ওকে বিভিন্ন হোটেলে বা ফার্মের মজুরদের ডেরায় মদ্যপ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। উঁচু-নিচু সব শ্রেণির মানুষের সাথে বসে মদ্যপান করে। সারাদিন মদের ওপরই থাকে। অপরিচিত মানুষের সাথে অনর্গল কথা বলতে ভালো লাগে ওর। আর এর সুবিধার্থে মদ্যপান করে মস্তিষ্ককে উত্তেজিত রাখে। ঐসব মানুষের সাথে বেশি বকবক করে যারা কখনো কোন ব্যাপারে বিরোধিতা করে না। তবে শুধুমাত্র এ-জাতীয় মানুষের সাথে বকবক করার সুবিধার্থেই, নাকি নিছক মাতাল হওয়ার জন্য, ঠিক কোন কারণে যে সে মদ্যপান করে তা বলা মুশকিল।
বাড়ির টাকা-পয়সার হিসাব নারী সম্প্রদায়ের কাছেই থাকে। ফলে টাকা জোগাড় করতে ফার্মের জিনিসপত্র বেচতে শুরু করল ফ্রিদিওফ। শেষ। পর্যন্ত নিজের সিন্দুক থেকেও জিনিসপত্র সরাতে লাগলো।
ইতোমধ্যে বাড়িতে একজন নতুন কেয়ারটেকার রাখা হয়েছে। আগের কেয়ারটেকারকে অসংলগ্ন আচরণের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে। নতুন লোকটা ভীষণ গোঁড়া। চার্চে নিয়মিত যাতায়াত তার। এখানে এসেই স্থানীয় পাদ্রিদের সহায়তায় মদের দোকানের লাইসেন্স বাতিল করিয়েছে। এতে ফ্রিদিওফ পড়লো মহা ফাঁপরে নতুন আখড়া খুঁজতে হল। অবশ্য পেতেও খুব-একটা দেরি হল না–ফার্মের মজুরদের ডেরায় বসে গেল। একের পর এক নতুন নতুন কেলেঙ্কারি রটতে লাগলো। ফ্রিদিওফ ওসবের তোয়াক্কা করে না। দিনে দিনে ও এমন পাড় মাতাল হয়ে গেল যে মদ্যপান করতে না-দিলে শরীরে খিচুনি শুরু হয়ে যায়।
শেষ পর্যন্ত ফ্রিদিওফকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হল। কিন্তু বিশেষ লাভ হলো না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিরাময় অযোগ্য রোগী হিসেবে ওকে আলাদা করে ফেলা হলো।
*** *** ***
সময় পেলেই ফ্রিদিওফ এখন জীবনের দিকে ফিরে তাকায়। পুরো জীবনকে একনজরে দেখতে চায়। সবাইকে নিয়েই চিন্তা করে নিজেকে নিয়ে, পরিবারকে নিয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে, সবকিছু নিয়ে। সবচেয়ে মন খারাপ হয় মেয়েদের কথা চিন্তা করলে ভবিষ্যৎ স্বামীকে না চিনে, তার প্রতি কোন ভালোবাসা না-থাকা সত্ত্বেও যেসব মেয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়, তাদের কথা চিন্তা করলে মনটা করুণায় ভরে যায়। ফ্রিদিওফ জানে এই অনুভূতি কতটা গভীর; কারণ, নিজের জীবন দিয়ে এ-অনুভূতির গভীরতা মেপেছে সে। এ-অনুভূতি এক অভিশাপের নামান্তর, যে অভিশাপ প্রকৃতির কোন নিয়ম ভঙ্গ করলে পেতে হয়। ফ্রিদিওফের বেলাতেও প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে। তাই এখন তার সমস্ত দুঃখের কারণ হিসেবে সে পরিবারকে দায়ী করে–“সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে, পরিবার কখনোই একটি শিশুকে যথাসময়ে স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেয় না।”
স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই ফ্রিদিওফের–পবিত্র অনুশাসনের দোহাই দিয়ে বিয়ের নামে যেসব শর্তাবলী চাপিয়ে দেয়া হয়, সেগুলোর ভারে তার স্ত্রী-ও কি সমানভাবে জর্জরিত হয়নি?
বিবাহিত এবং অবিবাহিত
হেমন্তের এক চমৎকার সন্ধ্যায় স্টকহোমের হোপ গার্ডেনের পথে পায়চারি করছিল ব্যারিস্টার তরুণটি। পাশের প্যাভিলিয়ন থেকে টুকরো-টুকরো গানের সুর ভেসে আসছিল। সেই সাথে মস্ত জানালার ফাঁক গলে আলোর বন্যা আছড়ে পড়ছিল রাস্তার ওপরের গাছটায়। সে-গাছে তখন হলদে ফুলের ছড়াছড়ি। আলো আর ফুল মিলে এক অপূর্ব প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয়েছে।
তরুণটি প্যাভিলিয়নের মধ্যে প্রবেশ করল। নিরিবিলি দেখে একটা টেবিলে বসে এক গ্লাস পাঞ্চ অর্ডার দিল। ইতোমধ্যে, সেখানে এক গায়কের অবির্ভাব ঘটল। একটা মৃত ইঁদুরকে নিয়ে লেখা খুব করুণ একটা গান গাইল সে। তাঁর পর এল এক তরুণী। উজ্জ্বল-গোলাপী-রঙের-জামা পরা তরুণীটি এসে একটা ড্যানিস গান গাইতে শুরু করল :
“জ্যোৎস্না ভরা রাতের চমৎকার যে ভ্রমণ
কোনকিছুই হয় না আনন্দের তেমন”
তরুণীটিকে দেখে সহজ-সরল বলেই মনে হল। গানটা সে ব্যারিস্টার তরুণটিকে উদ্দেশ করে গাইল। তাকে নিয়ে আলাদা করে এভাবে গান গাওয়ায়, তরুণটি বেশ লজ্জা পাচ্ছিল। তবে, খানিক গর্ববোধও হচ্ছিল তার। বলা যায়, একরকম ভালোই লাগছিল। যাহোক, কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের মধ্যে আলাপ জমে উঠল। এ আলাপের শুরু হয়েছিল এক বোতল মদ দিয়ে, আর শেষ হল দুই রুমের ঝাঁ চকচকে এক ফ্ল্যাটে গিয়ে। তরুণের অনুভূতি কেমন ছিল, কিংবা, ফ্ল্যাটের মধ্যে কী কী আসবাব আর সুযোগ-সুবিধা ছিলো তা পুরোপুরি বর্ণনা করা এ ছোটগল্পের সাধ্যাতীত। তবে, সর্বোপরি বলা যায়, ঐ দিনের পর থেকে তারা খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেল। অধুনা সমাজতান্ত্রিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, আর বান্ধবীকে সব সময় চোখে। চোখে রাখার বাসনায় তরুণটি সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে সে ঐ ফ্ল্যাটেই থাকবে। আর ঘরদোর গুছিয়ে রাখতে তার বান্ধবী থাকবে ফ্ল্যাটের। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে। বান্ধবীকে এতে বেশ খুশি বলেই মনে হল।
তরুণটির পরিবার কিন্তু এতে বাধ সাধল। তাদের মতে, সে অনৈতিক কাজ করে সবার মুখে চুনকালি দিয়েছে। অতএব, তাকে বকাঝকা করার জন্য বাবা-মা-ভাই-বোনদের সামনে তলব করা হল। কিন্তু তরুণের মনে হলো, সে এখন নিজে সিদ্ধান্ত নেবার মত যথেষ্ট বড় হয়েছে। সুতরাং, পরিবারের কথায় সে কোন রকম কর্ণপাত করলা না। ফলাফল যা হবার তা-ই হল: ‘পরিবারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ।
কিন্তু তরুণের জীবনে এর প্রভাব পড়ল উল্টোভাবে। ছোট্ট ফ্ল্যাটটিকে নিয়েই সে তার জগৎ কল্পনা করতে শুরু করল। একেবারে আদর্শ ঘরকুনো স্বামীতে(!), দুঃখিত, প্রেমিকে পরিণত হল। দুজনে বেশ সুখে সময় পার করছিল। একে অন্যকে প্রচণ্ড ভালোবাসত তারা, অথচ তাদের মধ্যে কোন আনুষ্ঠানিক বন্ধন ছিল না। ফলে, হারানোর ভয়টা সব সময়ই কাজ করত। আবার, এই হারানোর ভয় ছিল বলেই নিজেদের ভালোবাসাকে অটুট রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করত। বস্তুত, তারা ছিল দুই দেহ এক আত্না।
একটা জিনিসের অভাব অবশ্য ছিল–তাদের কোন বন্ধু ছিল না। সমাজের কারও তাদের প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না। ফলে, তারা কখনো কোথাও নিমন্ত্রিতও হত না।
*** *** ***
ক্রিসমাসের ঠিক আগের দিন।
যাদের এক সময় পরিবার ছিল, অথচ এখন নেই, তাদের জন্য এ দিনটা খুবই বেদনাদায়ক। সকালবেলা নাস্তার টেবিলে বসে তরুণটি একটা চিঠি হাতে পেল। বোনের চিঠি। ক্রিসমাসের দিনটা বাড়িতে বাবা-মার সঙ্গে কাটানোর জন্য অনুরোধ করেছে সে। চিঠি পড়ে তরুণ ব্যারিস্টার ভীষণ আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল, আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল–সে কি বান্ধবীকে একা ফেলে যাবে নাকি? অবশ্যই না। বাবা-মা এর আগেও বেশ ক’বার তাকে ছাড়া ক্রিসমাস পালন করেছে। অতএব, এবার বান্ধবীকে একা ফেলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।
যা-হোক, মনের মধ্যে এ-জাতীয় নানা ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে সে কোর্টে চলে গেল।
লাঞ্চের বিরতির সময় এক সহকর্মী এসে পাশে বসল। বেশ শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, “ক্রিসমাসে বাড়ি যাচ্ছ নাকি?”
প্রশ্ন শুনে তরুণ ব্যারিষ্টার দপ করে জ্বলে উঠল। তার মানে, সহকর্মীরা তার অবস্থান সম্পর্কে জানে? যদি না-জানে, তাহলে এই লোক এই প্রশ্ন দিয়ে কী বোঝাতে চাইল?
সহকর্মীটি লক্ষ্য করল, তরুণ ব্যারিষ্টার কিছু না বলে রাগ-রাগ হয়ে একটা ভুট্টা ছাড়াচ্ছে; তাই উত্তরের আশা না-করেই তড়িঘড়ি করে বলল “না, মানে বলছিলাম যে, যদি না যাও, তাহলে তুমি চাইলে দিনটা আমাদের সঙ্গে কাটাতে পারো। তুমি বোধহয় জানো না, আমার একটা খুব আদরের বন্ধু আছে। অবশ্য, বন্ধু না বলে আমার আত্মা বলাটাই ভালো।”
কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছিল তরুণের। নিমন্ত্রণ সে গ্রহণ করতে পারে, তবে এক শর্তে–তাদের দুজনকেই নিমন্ত্রণ করতে হবে।
সে-তো বটেই। নিমন্ত্রণ করলে তো দুজনকেই করবে। সে আবার ভিন্নকিছু আশা করেছিল নাকি? যাহোক, এভাবেই তাদের বন্ধু না-থাকার সমস্যা, আর ক্রিসমাস দিনের সমস্যা দুই-ই মিটে গেল।
ঠিক ছয়টার সময় ওরা নতুন বন্ধুদের ফ্ল্যাটে পৌঁছল। সবার ব্যবহার বেশ আন্তরিক। পুরুষ দুজন যখন ‘পাঞ্চ’ পান করল, নারী দুজন তখন রান্নাঘর সামলালো। খাবার সময় হলে চারজনে ধরাধরি করে টেবিল পাতলো। কিন্তু টেবিলটা একসাথে চারজন বসে খাবার মত যথেষ্ট বড় ছিল না। এটা-ওটা জোড়া দিয়ে বড় করার চেষ্টা করেও যখন লাভ হল না, তখন পুরুষ দুজন হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসল।
নারী দুজন কিন্তু ইতোমধ্যে বেশ ভালো বন্ধু হয়ে গেছে। দুজনের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া হয়েছে। কারণ, তারা দুজনেই এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের প্রতি সমাজের করা অভিন্ন কটুক্তিই এই বন্ধনের মূল। তারা নিজেরা অবশ্য একে-অন্যকে বেশ সম্মান দিয়ে কথা বলল, অন্যের অনুভূতিগুলোর যথার্থ মূল্যায়ণ করল। সেইসঙ্গে, সতর্কতার সাথে সব রকম বিতর্কিত প্রসঙ্গ পাশ কাটিয়ে গেল। সাধারণত ছেলেমেয়েরা আশেপাশে না-থাকলে স্বামী-স্ত্রী যেসব বিষয়ে কথা বলে, বিবাহিত হওয়ার সুবাদে যেসব বিষয়ে কথা বলাকে নিজেদের অধিকার বলে মনে করে, সেসব বিষয়ও এরা সযত্নে এড়িয়ে গেল। এভাবে বেশ গুছিয়ে খাওয়াদাওয়া শেষ করল ওরা।
খাওয়ার পর্ব শেষে যখন পুডিং আনা হল, তখন তরুণ ব্যারিস্টার কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ালো–এই সমস্ত আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানালো। প্রশংসার সুরে বলল, “সেটাই হচ্ছে প্রকৃত আনন্দ, যা-কিনা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ছেড়ে, সমস্ত ঝামেলা থেকে বের হয়ে এসে, প্রকৃত বন্ধুদের সাথে করা হয়। কিন্তু কেন জানি হঠাৎ করে মেরী লুইসা(তরুণের বান্ধবী) কাঁদতে শুরু করল। কারণ জানতে চাইলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে ব্যারিস্টার তার মা-বোনদের মিস করছে। লুইসার কথায় ব্যারিস্টার কিন্তু মোটেও খুশি হতে পারল না। সে জোর দিয়ে বললো, মা বোনদের সে মিস-ততা করছেই না, উপরন্তু, তারা যদি সবকিছু মেনেও নিত, তবুও সে আশা করত, এই সময় তারা দূরে থাকবে।
আচ্ছা! তাই যদি হবে, তবে সে লুইসাকে বিয়ে করছে না কেন?
অদ্ভুত! এর মধ্যে আবার বিয়ের কথা এল কোত্থেকে? তারা কি বিয়ের চেয়ে খারাপ আছে নাকি?
না, তা নয়। কিন্তু তারা যে সমাজ-স্বীকৃতভাবে বিয়ে করেনি সেটাও তো সত্য।
সমাজ-স্বীকৃত বিয়ে? মানে, পুরোহিতের দেয়া বিয়ে? ছিঃ! তরুণটি মনে করে, ও-বিয়ে কোন বিয়েই নয়; কারণ একটা মানুষ কতগুলো পরীক্ষা পাশ করে পুরোহিতের কাজ নিলেই তার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিকতা ভর করে না। বিয়ে পড়ানোর সময় পুরোহিত যে মন্ত্রগুলো পড়ে, ওগুলো আসলে অর্থহীন-যুক্তিহীন নিছক কতগুলো বাজে কথা! আর এই বাজে কথাগুলোর জোরেই বিয়ে পবিত্র হয়ে যাবে?
তা না-হয় ঠিক আছে, লুইসাও হয়তো তা-ই মনে করে, কিন্তু তার মন যে মানতে চায় না। মনে হয় যেন কোথায় কী একটা গণ্ডগোল আছে! মানুষজন তার দিকে আঙ্গুল তুলে কথা বলে যে!
–বলুক, যার যা খুশি বলুক!
কিছুক্ষণ পর তরুণ ব্যারিস্টারের সাথে সোফিও গলা মেলালো। সে ইতোমধ্যে জেনে গেছে, ব্যারিস্টারের পরিবারের লোকজন তাদের সম্পর্ককে ভালো চোখে দেখে না। অতএব, সে মন্তব্য করল, “পরিবার পরিবারের জায়গাতেই থাকুক। প্রত্যেকের একটা নিজস্ব অবস্থান থাকে, সে অবস্থানের গণ্ডি অতিক্রম করা কারো জন্যই সমীচীন নয়।” ব্যারিস্টার এবং তার প্রেমিকা যেন খানিকটা সান্ত্বনা পেল এতে। আরও কিছুক্ষণ সেখানে। থেকে, গল্পগুজব করে, বেশ রাত্রি করে তারা নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরল।
ওরা এখন আগের চেয়েও বেশি সুখী। কারণ, এখন নতুন বন্ধু হয়েছে। সবকিছু নিয়ে ওরা এমন গোছালোভাবে থাকতে লাগলো যে, সমাজ-স্বীকৃত উপায়ে গঠিত অনেক পরিবারের চেয়ে ওদের সুখ বেশি বলে মনে হয়। দুজনের সেই বন্ধনহীন ভালোবাসা আগের মতই অটুট রয়েছে। প্রেমিক প্রেমিকার মত করেই দিন পার হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহজনিত কারণে যেসব ঝামেলা হয়, যেমন: একে-অন্যের সাথে রাগারাগি করা, ঝগড়াঝাটি করা, সেগুলো কখনোই ওদের মধ্যে হয় না।
*** *** ***
দু’-এক বছর একসাথে থাকার পর তাদের মিলন এক পুত্রসন্তানে আশীর্বাদপুষ্ট হল। অতএব, প্রেমিকার পদোন্নতি হল এবার সে এখন মা, এবং এই পরিচয়ের বাইরে অন্য সব কিছু সে মন থেকে মুছে ফেলল। সন্তান জন্মদানের সময় যে যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছে, আর জন্মদানের পর যে পরম মমতায় সন্তানকে লালন করতে হচ্ছে, সে অনুভূতিগুলোর গভীরতায় আগেকার স্বার্থপর অনুভূতিগুলো নিমজ্জিত হল। আগে সে মনে করত, জগতের সব ভাল জিনিস শুধু তার একার জন্য, অথচ, এখন স্বামীর(!), দুঃখিত, প্রেমিকের ভালোবাসায় ভাগীদার আসাতেও সে মোটেই দুঃখিত হল না। নতুন ভূমিকায় নিজেকে সে বন্ধুদের। চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ববান বলে ভাবতে শুরু করল। প্রেমিকের সঙ্গে আচার-আচরণ, মিলন, সবকিছুতে যেন আগের চেয়ে বেশি প্রত্যয় ফুটে উঠল।
স্বামী(!) একদিন এক আনন্দের সংবাদ নিয়ে এল রাস্তায় বড় বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দেখা গেল, বোন তাদের সব খোঁজ-খবরই জানে। ছোট্ট ভাতিজাটাকে দেখার জন্য সে ভীষণ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কথা দিয়েছে, খুব শীঘ্রই একদিন তাদের বাসায় আসবে। খবরটা শুনে লুইসা বেশ অবাক হলেও তৎক্ষণাৎ ঘরদোর পরিষ্কার করতে লেগে গেল। এ উপলক্ষে একটা নতুন ড্রেসেরও বায়না ধরল।
পুরো সপ্তাহ জুড়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলল। পদাগুলো। লণ্ডিতে পাঠানো হল, চুলা-দরজার হাতল সব ঘষে-মেজে ঝকঝকে করা হল। আসবাবপত্রের ওপরও একপ্রস্থ নতুন রঙ চড়ল। বোন এসে দেখুক, তার ভাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-মার্জিত রুচির একজনের সাথেই থাকে!
অবশেষে সেই দিনটা এল। বেলা ১১টায় বোনের আসার কথা। তার আগেই কফি বানিয়ে রাখলো লুইসা। যথাসময়ে বোনের আগমন ঘটল। থমথমে ভাবলেশশূন্য মুখে সে লুইসার সাথে হাত মেলালো। এরপর ঘরের আসবাবপত্রগুলো বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। কিন্তু কিছু খেতে রাজি হল না। এ-ঘর ও-ঘরে উঁকি দিল; কিন্তু ভাইয়ের বউয়ের(!) দিকে আর ফিরেও তাকালো না। তবে বাচ্চাটা নিয়ে সে বেশ আগ্রহ দেখালো। ওকে নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করল। তারপর, যেভাবে এসেছিল সেভাবেই আবার গটগট করে চলে গেল। পুরো সময়টা জুড়ে লুইসাও কিন্তু বোনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। তার কোট, জামা-কাপড়-গহনার দাম কী রকম হতে পারে ইত্যাদি সব হিসাব করা হয়ে গেছে। সেই সাথে, চুল কাটার একটা নতুন ধরনও শিখেছে। পরবর্তীতে ওভাবে চুল কাটানো যেতে পারে! যা-হোক, বোনের কাছ থেকে খুব আন্তরিক ব্যবহার সে নিজেও আশা করেনি; প্রথমবারের মত যে এসেছে সেটাই যথেষ্ট। অতএব, লুইসাকে সর্বোপরি খুশিই মনে হল। প্রচার করে বেড়ালো, স্বামীর(!) বোন তাদের সংসার দেখতে এসেছিল।
*** *** ***
দিন দিন ওদের ছেলেটা বড় হয়ে উঠছে। ইতোমধ্যে, লুইসা আবার গর্ভবতী হল। এবার ফুটফুটে এক কন্যাসন্তানের জন্ম হল। তার পর থেকে, লুইসা আগের চেয়েও গম্ভীর হয়ে গেল। বাচ্চাদের ভবিষ্যত নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তা হয়। বাচ্চাদের বাবাকে প্রতিদিন বোঝানোর চেষ্টা করে তাদের বৈধ বিয়ে না-হলে বাচ্চাদের ভবিষ্যত কখনোই সুরক্ষিত হবে না। ওদিকে, ব্যারিস্টারের বোনও ইঙ্গিত দিয়েছিল, তাদের একসঙ্গে থাকাকে যদি তারা বিয়ের মাধ্যমে বৈধতা দেয়, তবে পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের একটা সমূহ সম্ভাবনা আছে।
সবদিক বিবেচনা করে, এবং লুইসার দুই বছরের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে, অবশেষে তার প্রেমিক বিয়ে করতে রাজী হল। সন্তানদের মঙ্গলের স্বার্থে ওই যুক্তিহীন মন্ত্রগুলোর মাধ্যমে পড়ানো বিয়ে সে মেনে নেবে।
কিন্তু ছোট্ট একটা সমস্যা–“বিয়েটা হবে কোথায়?”
লুইসা চার্চের জন্য জোরাজুরি করল। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? চার্চে বিয়ে হলে তো সোফিকে নিমন্ত্রণ করা যাবে না। ওকে তো নিশ্চয়ই চার্চে ঢোকার অনুমতি দেবে না। “ইস! সোফির মত একটা মেয়ে!” কিন্তু লুইসা এতে দমল না। সে বরং বলল, “সন্তানের মঙ্গলের জন্য বাবা-মাকে ব্যক্তিগত অনেককিছুই ত্যাগ করতে হয়।” অতএব, শেষ পর্যন্ত তারই জয় হল।
বিবাহ সম্পন্ন হল! কিন্তু ব্যারিস্টারের বাবা-মার থেকে কোন নিমন্ত্রণ এলো না। এলো সোফির কাছ থেকে একটা চিঠি। এমন একটা কাজ করার জন্য, বিশেষত, তাকে নূন্যতম কিছু না-জানিয়ে করার জন্য সে ভীষণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। লুইসাদের সঙ্গে সে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না জানিয়ে দিয়েছে।
লুইসা অবশ্য এতে খুব একটা দুঃখিত হল বলে মনে হল না। সে এখন একজন বিবাহিতা নারী’, এটাই সবচেয়ে বড় কথা! কিন্তু কেন জানি নিজেকে তার আগের চেয়ে অনেক বেশি একাকী মনে হয়। অবশ্য, এক ধরনের স্বস্তিও আছে–তাদের সম্পর্কটা এখন বৈধ।
আর, এই স্বস্তিবোধ থেকেই সে সবরকম স্বাধীনতা ভোগ করতে শুরু করল। সেই-সব স্বাধীনতা, যেগুলোকে বিবাহিত মানুষ নিজেদের অধিকার বলে মনে করে। এক সময় যেগুলোকে সে স্বেচ্ছায়প্রাপ্ত উপহার বলে ভাবত, এখন সেগুলোকে নিজের প্রাপ্য বলে মনে করতে শুরু করল। প্রথমেই সে নিজেকে ‘সন্তানের মা পরিচয়ের আড়ালে ঢেকে ফেলল। আর, এখান থেকেই যেন তার নবযাত্রা সূচিত হল।
ওদিকে, স্বামী বেচারার মাথায় কিছুতেই ঢুকল না, ‘সন্তানের মা এই পরিচয়ের বিশেষ কী মাহাত্ম আছে! তাছাড়া, তার সন্তানেরা তো আর দশটা স্বাভাবিক সন্তানের মতই। তারা এমনকিছু নয় যে, তাদের মা হওয়াটা বিরাট গর্বের কোন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে! পুরো ব্যাপারটা স্বামীর কাছে একটা ধাঁধার মত হয়ে রইল। তবে, তার নিজের স্বভাবেরও খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে আজকাল। মনে কিছুটা খচখচানি থাকা সত্ত্বেও, সে আগের মত আবার বাইরের জগতের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হতে শুরু করেছে। অবশ্য, এর পেছনে যুক্তিও আছে–“সন্তানদের তো তখন একজন বৈধ মা রয়েছে। সুতরাং, বাইরের জগতের যে ব্যস্ততাগুলো সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, সেগুলো আবার শুরু করতে বাধা-তো নেই। মাঝে এগুলো ভুলে যাওয়ার কারণ ছিল প্রথমত, সন্তান হবার আগে সে প্রেমের মায়ায় বিভোর থাকত; দ্বিতীয়ত, সন্তান হবার পর প্রেমিকা আর সন্তানদের রেখে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারটাকে সে রীতিমত ঘৃণা করত। এখন যেহেতু সব অনিশ্চয়তা কেটে গেছে, এখন বাইরে যাওয়াই যায়।
স্বামীর এই অবাধ স্বাধীনতা স্ত্রীর কিন্তু মোটেও পছন্দ হল না। আগে থেকেই সে ছিল স্পষ্টবাদী স্বভাবের, আর এখনতো এমনিতেই গোপন করার কিছু নেই। অতএব, যা কিছু মনে হয় সবকিছু চটপট স্বামীকে বলে বসে। স্বামী কোনরকমে ব্যাপারগুলোকে মোটামুটি ম্যানেজ করে নেয়। ওকালতির পাঁচ ভালোই জানা আছে তার। স্ত্রীর উল্টাপাল্টা কথাবার্তায় বিব্রত না হয়ে, বরং বেশ বুদ্ধিদ্বীপ্ত উত্তর দেয় সে।
একদিন স্ত্রী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, “ঘরে বউ রেখে বাইরে-বাইরে ঘোরাটা কি ঠিক?”
“হুম! কিন্তু সে-জন্য তোমরা আমাকে মিস কর বলে তো মনে হয়!” স্বামী কোনমতে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলাল।
–তোমাকে মিস করি কি না? বর যখন ঘর-সংসার দেখাশোনার টাকা মদ খেয়ে ওড়ায়, বউ তখন ঘরে অন্য আরও অনেক জিনিস মিস করে।
–আচ্ছা! তাই নাকি? তবে শোন, প্রথমত, আমি মদ খাই না; মাঝে মাঝে বাইরে থেকে এটা-ওটা কিনে খাই, আর কিঞ্চিৎ কফি পান করি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আমি ঘর-সংসার দেখাশুনার টাকা ওড়াইনা; কারণ, সেটা। তোমার কাছেই সযত্নে গচ্ছিত থাকে। পানভোজনের টাকার জন্য আমার। অন্য তহবিল আছে।”
শেষের কথাগুলো স্বামী ঠাট্টাচ্ছলে স্ত্রীর সুর নকল করে বলল।
দুর্ভাগ্যবশত, মেয়েরা কখনোই ঠাট্টা ব্যাপারটা বোঝেনা। ফলে, মজার। ছলে স্বামী যে ফাঁস তৈরি করেছিল, কিছুক্ষণ পর সেটা তার নিজের গলায়ই এসে পড়লো।
–‘পানভোজন!’ তার মানে তুমি স্বীকার করছ, তুমি মাঝে মাঝে মদ খাও?
–মোটেও না। তোমাকে নিয়ে একটু মজা করার জন্য অমন করে বলেছি।
–আমাকে নিয়ে মজা করার জন্য? তার মানে, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে মজা করছ? কই, আগেতো কখনো এমন করতে না!
–আরে বাবা! তুমি নিজেই তো বিয়ে করতে চেয়েছিল; এখন আবার সবকিছু আগের চেয়ে আলাদা করে দেখছ কেন?
–আলাদা করে দেখছি, কারণ আমরা এখন বিবাহিত!
–এটা আংশিক কারণ। পুরো কারণটা হচ্ছে, তোমার মোহ এখন কেটে গেছে।
–আমাদের সেই সময়গুলোকে তোমার কাছে মোহ মনে হচ্ছে?
–শুধু আমার কাছে নয়, তোমার কাছেও; এবং জগতের সবার কাছেই। আসলে আগে-পরে যখনই হোক, এই মোহ একসময় কেটে যাবেই।
–আচ্ছা! তার মানেটা দাঁড়ালো এই যে, যখনই পুরুষের ঘাড়ে দায়িত্ব আসে, তখনই ভালোবাসা তার কাছে মোহ মনে হয়। তাই না?
–হুম! নারীর ঘাড়ে দায়িত্ব এলে তার কাছেও তা-ই মনে হয়।
“মোহ! শুধুই মোহ?” স্ত্রী বিড়বিড় করে বলতে লাগল।
এবারে স্বামী ঝটকা মেরে বলল, “তবে তার মানে এই নয় যে, দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকা যাবে না।”
“অর্থাৎ, বিয়ের প্রয়োজন নেই। তাই বলতে চাইছ তো?” স্ত্রী বেশ রেগে গেল ।
“ঠিক তাই। আমি তোমাকে ঠিক এই কথাটাই সব সময় বোঝাতে চেয়েছি।” স্বামীর স্পষ্ট জবাব ।
“কিন্তু তুমি নিজে কি চাওনি আমাদের বিয়ে হোক?” স্ত্রীকে আবেগী দেখালো ।
–চেয়েছি। তার একমাত্র কারণ, তিন-তিনটা বছর ধরে তুমি এ-নিয়ে আমার মাথা নষ্ট করে ছেড়েছ।
–কিন্তু এটাতো সত্য, তুমি চেয়েছিলে আমরা বিয়ে করি।
–কারণ, তুমি চেয়েছিলে; আর, শেষ পর্যন্ত সেটা পেয়েছ সে-জন্য তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।
–তুমি তোমার সন্তানদের মাকে ফেলে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও, এই জন্য আমাকে কৃতজ্ঞ থাকতে বলছ?
–মোটেই না; বরং, তোমাকে বিয়ে করেছি এই জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে বলছি।
–তুমি কি সত্যিই মনে কর, আমার সে জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত?
–হ্যাঁ, মানুষ নিজের পথ খুঁজে পেলে যেভাবে কৃতজ্ঞ থাকে, তোমারও। সেভাবে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।
“বেশ! তাহলে তুমিও শুনে রাখ, আমাদের এই বিয়ে কোন বিয়েই নয়। এ-বিয়েতে কোন সুখ নেই। তোমার পরিবার আমাকে স্বীকার করে না।” স্ত্রী রাগে ফেটে পড়ল।
–এর মধ্যে আবার আমার পরিবার এল কেথেকে? আমিতো কখনো তোমার পরিবার নিয়ে মাথা ঘামাইনি।
–মাথা ঘামাওনি, কারণ, তোমার মনে হয়েছে আমার পরিবার নিয়ে কখনো কোন চিন্তা-ভাবনা না করলেও চলবে।
–আচ্ছা! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন, আমার পরিবার নিয়ে সবসময় তোমার ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা ছিল! এমনকি তারা যদি মুচি চামারও হত, তবুও তাদের নিয়ে তুমি সুখে থাকতে!
–এমনভাবে কথা বলছ যেন মুচি-চামাররা মানুষ না। অন্যদের মত ওদের বাঁচার অধিকার নেই?
–অবশ্যই আছে। তবে আমার মনে হয় না, মুচিদের প্রতি দরদ দেখিয়ে, তুমি ওদের সাথে গিয়ে থাকতে রাজি হতে…
কথা কাটাকাটির এই পর্যায়ে স্ত্রী চিৎকার করে উঠল–“ঠিক আছে! সব ঠিক আছে! তুমি তোমার মত থাক, আমি আমার মত থাকবো।”
আসলে কিন্তু সব ঠিক ছিল না। আসলে, আর কখনোই সব ঠিক হয়নি।
*** *** ***
আচ্ছা, এই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ কি তবে বিয়ে? নাকি অন্য কিছু?
লুইসা শেষ পর্যন্ত স্বীকার না করে পারেনি, তাদের আগের সময়টাই ভালো ছিল। সে সময় তারা সুখী ছিল।
স্বামীরও মাঝে মাঝে মনে হয়, তাদের সম্পর্কের বৈধতা দেয়ায়, অর্থাৎ, বিয়ে করার কারণেই অশান্তিটা হয়েছে। কারণ, সে যত বিবাহিত দম্পতি দেখেছে, তাদের সবাই-ই অসুখী। তবে, সবচেয়ে কষ্টকর বিষয়টি সে বুঝতে পারল যখন সেই পুরনো বন্ধু আর সোফির ব্যাপারে জানলো। বিয়ের পর প্রায়ই সে স্ত্রীকে না-জানিয়ে ওদের বাড়িতে যেত। তেমনি একদিন ওদের বাড়িতে গিয়ে জানতে পারল, ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। “অথচ ওরা কখনো বিয়েই করেনি!”
তার মানেটা দাঁড়ালো এই, সত্যিকার দোষটা আসলে বিয়ের নয়।
মুখবন্ধ
সময়টা নারী অধিকার আন্দোলনের মোটামুটি গোড়ার দিকের। হেনরিক ইবসেনের ‘এ ডলস হাউস’(১৮৭৯) চারদিকে ভীষণ সাড়া ফেলেছে তখন। নারীনেত্রীরা এবং অতি অবশ্যই নারীবাদীরা একে যেন রাতারাতি নিজেদের আন্দোলনের ম্যানিফেস্টো বানিয়ে ফেললেন। নোরার গৃহত্যাগ যেন গোটা ইউরোপীয়-নারী-সমাজের আদর্শ হয়ে উঠল। সেই সাথে নারী অধিকার আন্দোলনেও যোগ হতে থাকল নতুন নতুন মাত্রা। সমাজ, সংসার, বিয়ে সবকিছুকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তাঁরা; নানা অসংগতি আর জটিলতা খুঁজে বের করতে থাকলেন। কিন্তু এ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের কখন যে তাঁরা ‘এক্সট্রিমিস্ট’ হয়ে উঠলেন, তা নিজেরাও বুঝতে পারলেন না। ফলে, জগৎ সংসারের সমস্ত দোষ গিয়ে পড়ল পুরুষের ঘাড়ে! আর, নারীর অবস্থান হল যাবতীয় সমালোচনার উর্ধ্বে। ফলে, এ আন্দোলনে বস্তুত নিরপেক্ষতা বলতে কিছু রইল না, এবং স্বাভাবিকভাবেই নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানো হল। বাড়তে থাকল বিবাহ-বিচ্ছেদ আর সাংসারিক অশান্তি…
কিন্তু আসলেই কি সব দোষ পুরুষের? কিংবা, সব দোষ নারীর বললেও কি তা যথার্থ হবে? নাকি, দোষ-ত্রুটিগুলো সম্পূর্ণ মানবিক এবং প্রাকৃতিক? এ প্রশ্নগুলোই অগাস্ট স্ট্রিনডবার্গ তুললেন তাঁর ছোটগল্পের মাধ্যমে। ঐ সময় অবশ্য কোন বই আকারে তিনি গল্পগুলো লেখেননি, বরং, প্রতিটি গল্প আলাদাভাবে প্রকাশিত। পরবর্তীতে, ১৮৮৪ সালে এরকম বেশ কতগুলো গল্পকে ‘গেটিং ম্যারেড’ নামে দু’মলাটে আবদ্ধ করা হয়। যে-কারণে কতগুলো গল্পের কাহিনিতে কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অবশ্য, এর অন্য কারণও ছিল–ঐ সময়ে নারীবাদীরা উঠেপড়ে লেগেছিলেন ‘বিয়ে’ সম্পর্কটাকে ‘মালিক-দাসী’ সম্পর্ক হিসেবে দেখাতে। স্ট্রিনডবার্গের কাছে একে নিতান্ত অমূলক মনে হয়েছে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের পরিপূরক; কেউ কারো মালিক বা দাসী নয়, বরং, ক্ষেত্রভেদে একে-অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতা মানে অক্ষমতা নয়, ভালোবাসার পূর্ণতা। নারী-পুরুষকে নারীবাদীরা যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়েছেন, স্ট্রিনডবার্গ সেখানে খুঁজে পেয়েছেন সহযোগিতা।
এ ডলস্ হাউস গল্পটি স্ট্রিনবার্গ লিখেছিলেন হেনরিক ইবসেন লিখিত ঐ একই নামের বিখ্যাত নাটকটির প্রতিক্রিয়া হিসেবে। যদিও অতি সাম্প্রতিককালে নাটকটির বিষয়বস্তু নিয়ে কিছুটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে; প্রশ্ন উঠেছে–ইবসেন নিজে নোরাকে অধিকারবঞ্চিত দেখাতে চেয়েছেন, নাকি নারীবাদীরা নিজেদের মত ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে নিয়েছেন? (কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের Female Power and Some Ibsen Plays ago দ্রষ্টব্য) কিন্তু ঐ সময়ের প্রচলিত ব্যাখ্যায় (নারীবাদী ব্যাখ্যা) স্ট্রিনবার্গ ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। সে-কারণেই, ঐ নামের ছোটগল্প লিখে দেখাতে চাইলেন–নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলা মানেই নারীদের প্রতি কোন অন্ধ পক্ষপাতিত্বে পৌঁছানো নয়। সংসারে ভুল-ত্রুটি সবারই থাকে, একে যেকোন একপক্ষের বিরুদ্ধে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করাটা আসলে এক ধরনের গোড়ামি।
পরিবর্তনের প্রচেষ্টায়, দেনা-পাওনা, বিবাহিত এবং অবিবাহিত, এবং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা গল্পগুলোতে স্ট্রিনবার্গ ঐ সময়ের তথাকথিত নারী আন্দোলনকে ব্যাঙ্গ করেছেন। নারীবাদীরা কীভাবে ভীষণ অযৌক্তিক আচরণ করেছেন সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। ফলে, এ গল্পগুলোর কাহিনি মোটামুটি একই রকম–প্রতিটি গল্পে তিনি নারীবাদীদের ‘আদর্শ সংসার’ কে প্লট হিসেবে নিয়েছেন; অতঃপর বাস্তবতার আলোকে সে ‘আদর্শ সংসার’ ধারণার ত্রুটিগুলো দেখিয়েছেন।
স্ট্রিনডবার্গের নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকার প্রচেষ্টা ফুটে ওঠে ক্ষতিপূরণ, বিবাহ অনিবার্য এবং ফিনিক্স গল্পগুলো পড়লে। এ গল্পগুলোতে, তিনি পুরুষের দোষগুলো সামনে এনে নারীর অবস্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। সেইসঙ্গে, সামনে এনেছেন এক নির্মম সত্যকে নারী-পুরুষের অবস্থানগত দ্বন্দ্ব যদি থেকেই থাকে, তবে তার দায় এককভাবে নারী বা পুরুষ কারোরই নয়, বরং, চিরায়ত এ অবস্থান তৈরিতে পরিবার এক বিরাট ভূমিকা রাখে, যেখানে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রকট হয় নারীরই আরেক রূপ (বউ-শাশুড়ি, ননদ-ভাবী ইত্যাদি)। তাই, সত্যিকার পরিবর্তন চাইলে, পরিবর্তনটা আনতে হবে পরিবার সম্পর্কিত সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনায়, শুধুমাত্র পুরুষের দিকে আঙুল তুললে সেটা অন্যায় হবে।
অপ্রাকৃতিক নির্বাচন এবং রোমিও অ্যান্ড জুলিয়া গল্প দুটোর প্লট সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমটিতে উঠে এসেছে শ্রেণি-বৈষম্য, এবং সেইসাথে আবারও প্রমাণিত হয়েছে, স্ট্রিনডবার্গ সবসময়ই নির্যাতিতের পক্ষে ছিলেন। তাঁর কলম সব সময় ন্যায়ের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে। দ্বিতীয় গল্পটি একটি মধুর দাম্পত্য সম্পর্কের গল্প। হয়ত, এটাই স্ট্রিনডবার্গের ‘আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্ক, যেখানে ভালোবাসা আছে, আবার ভিন্নমতও আছে; রোমন্থন আছে, খুনসুটিও আছে, এবং দিনশেষে অবশ্যই দুজনের মুখে হাসি আছে।
যাহোক, প্রতিটি গল্পে স্ট্রিনর্গের বিশ্লেষণী ক্ষমতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। গল্পগুলোতে হয়ত কিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়; কিংবা, কিছু গল্পে হয়ত হেনরিক ইবসেনকে একটু বেশিই খোঁচানো হয়েছে; তবু মানতেই হয়, নারী অধিকারের দোহাই দিয়ে যে ‘এক্সট্রিমিজম’ শুরু হয়েছিল তা থেকে বেরিয়ে এসে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ করে দেয় অগাস্ট স্ট্রিনবার্গের ‘গেটিং ম্যারেড’।
“এক ভাষার সাহিত্যকর্ম অন্য ভাষায় পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলা কখনোই সম্ভব নয়” কথাটা হয়ত আংশিক সত্য। পুরো সত্যটা হচ্ছে, সাহিত্যরস আস্বাদনের ক্ষমতা যার রয়েছে তার জন্য ভাষা কোন বাধা নয়। ব্যক্তিগত জীবনে অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ মানুষটা ছিলেন ক্ষ্যাপাটে প্রকৃতির। তাঁর লেখাতেও সে ছাপ বেশ গাঢ়ভাবেই পাওয়া যায়। তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে আমি তাই দেখার চেষ্টা করেছি সেই ক্ষ্যাপাটে মানুষটাকে, বুঝতে চেয়েছি তাঁর বোধকে। গল্পগুলো অনুবাদ করতে গিয়েও এ-স্বাধীনতাটুকু আমি অক্ষুণ্ণ রেখেছি–পাঠকের সামনে স্ট্রিন্ডবার্গকে মূর্তিমান করতে তাঁর গল্পের বক্তব্যকেই অনুবাদ করেছি, লাইনকে করিনি। আশা করি, পাঠক একে সুদৃষ্টিতে দেখবেন। তবুওততা একদিনে ‘মেঘনাদবধ হয় না–গল্পগুলোর অনুবাদে কোথাও কোন অসঙ্গতি চোখে পড়লে নির্দ্বিধায় জানাবেন। পরবর্তী অনুবাদকে আরও সমৃদ্ধ করতে আপনাদের পরামর্শগুলো পথনির্দেশনা হিসেবেই গৃহীত হবে।
মূল বইয়ের সবগুলো গল্পের অনুবাদ এখানে নেই। বাছাইকৃত দশটি গল্প নেয়া হয়েছে। ফলে মূল নামটিও–গেটিং ম্যারেড–এখানে ব্যবহার করা হয়নি। বরং বইয়ের সবচেয়ে আলোচিত–এ ডলস্ হাউস–গল্পটিই বইয়ের শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাঠকের গ্রহণ/অগ্রহণই বলে দেবে অবশিষ্ট গল্পগুলোর পরিণতি কী হবে…
মাহবুব সিদ্দিকী
ঢাকা
২২ আগস্ট ২০১৬ ইং
ভূমিকা
অগাস্ট স্ট্রিনবার্গ বাংলাদেশী পাঠক মহলে খুব বেশি পরিচিত না হলেও বিশ্বসাহিত্যে অত্যন্ত সমাদৃত একজন সৃজনশীল মানুষ। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি শাখায় বিচরণ থাকলেও মূলত নাট্যকার হিসেবেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেশি। এ বইতে অবশ্য পাঠক তাঁর গল্পকার সত্তার সঙ্গেই পরিচিত হবেন। তবে, আমার কাছে অগাস্ট স্ট্রিনড়বার্গ সবসময়ই একজন প্রতিবাদী মানুষের প্রতিভূ। সে অর্থে আমাদের নজরুলের সঙ্গে তাঁর ভীষণ সাযুজ্য খুঁজে পাই, যিনি সকল প্রতিকূলতার মাঝেও সাম্যের গান গেয়েছেন, বলেছেন–“বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।” কিন্তু সাম্যের নামে যখন নারী-পুরুষকে পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী দেখিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা, দায়িত্ব-কর্তব্য, সমঝোতাকে দাঁড়িপাল্লায় তোলা হতে লাগলো, হেনরিক ইবসেনের তথাকথিত ‘নারীবাদী নাটকগুলোর দোহাই দিয়ে সম্পর্কগুলো সংজ্ঞায়িত হতে লাগলো এককভাবে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে, তখনই অগাস্ট স্ট্রিনবার্গ তাঁর চিরচেনা প্রতিবাদী মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। পাঠকের সামনে উপস্থাপন করলেন এমন কিছু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ বিষয়কে যেগুলো এড়িয়ে গিয়ে কতিপয় গত্বাঁধা স্থূল-বিষয় নিয়ে সে সময় নারী আন্দোলন দানা বাঁধছিল। স্ট্রিনডবার্গ মনে করতেন, আন্দোলন ব্যাপারটি নিরপেক্ষ; এর শুরুতে ‘নারী বা ‘পুরুষ যেকোন শব্দ জুড়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে সেটিকে একপাক্ষিক করে ফেলা, আর এ ধরনের আন্দোলনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় পোষণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যদিও স্ট্রিনড়বার্গের ব্যক্তিগত জীবন পর্যালোচনায় দেখা যায়, জীবনের এক পর্যায়ে তিনি ভীষণ নারী-বিদ্বেষী হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেসময় তিনি পুরোপুরি মানসিক বিকারগ্রস্থ ছিলেন এবং তাঁর গল্পগুলো সে সময়ের অনেক আগে লেখা। যাহোক, আমার মনে হয় বাংলাদেশেও বর্তমানে স্ট্রিনর্গের সময়ের মত একটি একপেশে ধারা চলছে। অনেকটা বোধহয় জোর করেই নারী-পুরুষ সম্পর্কটাকে বারবার আতশি কাঁচের নিচে আনা হচ্ছে এবং পুরুষ কিংবা পুরুষতান্ত্রিক শব্দগুলোকে ঋণাত্বক হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ চেষ্টার চালিকাশক্তি হিসেবে গতানুগতিকভাবেই হেনরিক ইবসেনের নাটকগুলোকে ব্যবহার করা হয়। অথচ ইবসেনের বক্তব্য যে ভিন্ন আঙ্গিক থেকেও উপস্থাপন সম্ভব, কিংবা নাটকগুলোর সূক্ষতর বিশ্লেষণ যে অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের বিপক্ষে যেতে পারে এই চিন্তাটি কিন্তু করা হয় না। আমি অবশ্য মনে করি, কোন বিষয়ে নারী বা পুরুষ যে কারো ভুল দেখতে পাওয়া মানেই তার অবস্থান নিচু বা ঋণাত্বক হয়ে যাওয়া নয়। এতে বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা মনুষ্যত্বের সীমার মধ্যেই রয়েছেন, কারণ, “মানুষ মাত্রই ভুল হয়।” কিন্তু এই ভুলগুলোকে যারা খুব বেশি বড় করে তোলেন তারা বুঝতে চান না–বিপরীতপ্রান্তে দাঁড়ানো মানুষটিকে ক্রমাগত অসহনীয় হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা প্রকারান্তরে নিজের অবিবেচকতাকেই প্রকট করে তোলা। তাই, সময় এসেছে ‘জেন্ডার বিষয়টিকে নতুনতর আলোকে চিন্তা করার; এবং তার অংশ হিসেবে স্ট্রিনবার্গ-পাঠ যথেষ্ট ফলদায়ী হবে বলেই আমার ধারনা। সে হিসেবে স্ট্রিনবার্গের গল্প নিয়ে বই প্রকাশ করা একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বলে মনে করছি।
আমাদের দেশে অনুবাদ-সাহিত্য দীর্ঘদিন ধরেই একটি বিকাশমান মাধ্যম। বলা হয়ে থাকে, মৌলিক লেখার চেয়ে অনুবাদের ক্ষেত্রে মেধা, মনন আর শ্রমের খরচ বেশি হয়। অনুবাদ কেবলমাত্র ভাষান্তর নয়, এর সঙ্গে ভাবেরও প্রয়োজন। এজন্য অনুবাদকের সাহিত্যজ্ঞান প্রখর হওয়া আবশ্যক। অন্যথায়, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় লেখা রূপান্তরিত হবে ঠিকই, কিন্তু লেখার মাঝে প্রাণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে। একটি সার্থক অনুবাদ তার শিল্পগুণে হয়ে ওঠে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যকর্ম। তাই স্বপ্রণোদিত হয়ে অনুবাদের দীর্ঘযাত্রার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার অভিলাষে যারা উদ্যোগী হন, তাদের সাধুবাদ জানানো প্রত্যেক সচেতন বইপ্রেমির নৈতিক দায়িত্ব হওয়া উচিত। অনুবাদক শুধু বিদেশী সাহিত্যটিকে নয়, সেদেশের সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, ব্যক্তিসম্পর্ক, প্রতিবেশের সাথে নিজ ভাষার পাঠককে পরিচিত করানোর ভূমিকাটিও পালন করেন। সে বিবেচনায় অনুবাদক আদতে একজন ভ্রমণ প্রদর্শক। পাঠকের প্রশান্তিই অনুবাদকের পরিতৃপ্তি।
মাহবুব সিদ্দিকী বয়সে তরুণ, নিজে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন এবং পেশাগত জীবনেও তার ছাপ বজায় রাখতে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। পেশাদার অনুবাদক তিনি নন, আমি বলবো এটি একটি শুভবার্তা। কারণ, পেশাদার অনুবাদক মানে এই কাজটির মাধ্যমেই তার জীবিকার সংস্থান হয়। ফলে, যত বেশি সম্ভব অনুবাদ তাকে করতে হয় একটি সীমিত ব্যবধিতে। সেক্ষেত্রে কোয়ালিটি বনাম কোয়ান্টিটি এর চিরন্তন সংঘাতে তাকে মধ্যবর্তী একটি সমঝোতায় আসতে হয়। মাহবুব সিদ্দিকীর সেই বাস্তবতা নেই, তিনি অনুবাদ করেছেন গভীর আন্তরিকতা থেকে। ফলে, যত্ন এবং নিষ্ঠার সমন্বয়ে গুণগত উৎকর্ষের একটি মাত্রায় পৌঁছতে তাঁর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। আমার সুযোগ ঘটেছিল তাঁর অনুবাদের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিটি পড়বার। পাঠ পরবর্তীতে অনুবাদের কিছু অংশের ব্যাপারে তাঁকে মতামত দিই যেখানে আরেকটু উন্নতির সুযোগ রয়েছে। সেই পরিক্রমায় জানতে পারি, শুধু আমি একা নই, তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠকের তালিকায় ছিলেন আরও বেশ ক’জন সাহিত্যানুরাগী, যাদের প্রত্যেকের মতামতের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল থেকে অনুবাদে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনার কাজটি করা হয়েছে। একটি অনুবাদ প্রকল্পে এতজন মানুষের মতামত নিয়ে সেই অনুযায়ী সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া কাজটির প্রতি অনুবাদকের শতভাগ নিবেদনকেই স্বতঃসিদ্ধ করে। তাই, মাহবুব সিদ্দিকী ভবিষ্যতেও অনুবাদের কাজটি অব্যাহত রাখলে আমাদের অনুবাদ-সাহিত্য যে আরও সমৃদ্ধ হবে এ ব্যাপারে নিঃসংশয়েই অভিমত ব্যক্ত করা যায়। প্রতিক্রিয়া একজন শিল্পীর কাজের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। অনুবাদকও তো একজন শিল্পীই বটে।
যেহেতু এটি তাঁর প্রথম কাজ, পাঠক যদি উৎসাহসূচক মতামত দেন সেটি হয়তো তাঁর অন্তর্নিহিত শিল্পচেতনাকে আরও তেজোদ্দীপ্ত করবে। আমাদের দেশে অভিযোগ করা মানুষের সংখ্যা অগণিত, তুলনায় উৎসাহ দেবার মানুষের সংখ্যা কম। এই সরলীকৃত প্রবণতার বাইরে থেকেই পাঠক তরুণ অনুবাদকের প্রয়াসকে মূল্যায়ন করুক, এটিই প্রত্যাশা। অগাস্ট স্ট্রিনর্গের প্রতি আরও একবার শ্রদ্ধা জানাই, এবং সেই সাথে মাহবুব সিদ্দিকীর জন্যও শুভকামনা রইলো।
ড. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কৃতজ্ঞতা
শ্রদ্ধেয় ড.কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় স্যার, যার সুবাদে অগাস্ট স্ট্রিনডবার্গকে চিনেছি। স্যার না-থাকলে হয়ত স্ট্রিনবার্গ আমার কাছে ‘স্ট্রেঞ্জার থেকে যেত। সেই সঙ্গে, আরও একজন মানুষের নাম না করলেই নয়–শ্রদ্ধেয় শেখ আলাউদ্দিন স্যার। গল্পগুলো ছাপার অক্ষরে পাঠকের হাতে পৌঁছানোর আগে স্যার পড়ে না-দিলে বুঝতেই পারতাম না, ‘আ-কার, ‘এ-কার’, ‘হ্রস্ব ই কার’, ‘দীর্ঘ ঈ-কার’ নিয়ে আমার দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি রয়েছে।
ভাইয়া (মাহফুজ সিদ্দিকী) কে আনুষ্ঠানিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানালে সেটা ন্যাকামো হবে কি না জানি না, ভাইয়া হয়ত পাকামোও বলতে পারে; তবুও, গল্পগুলো পড়ে দিয়ে, দরকার মতো মন্তব্য করে এবং আরও নানাবিধ উপায়ে সহযোগিতা করে এগুলোর কাঠামো দাঁড় করাতে ভাইয়া যে ভূমিকা রেখেছে সেজন্য আমার পক্ষ থেকে যেকোনো রকম অনুভূতি প্রকাশ পেলে দিনশেষে তার নাম কৃতজ্ঞতা-ই হবে।
মাহবুব সিদ্দিকী
ঢাকা
২৩ আগস্ট, ২০১৬
অগাস্ট স্ট্রিনডবার্গ
অগাস্ট স্ট্রিনডবার্গকে বলা হয় আধুনিক সুইডিশ সাহিত্যের জনক। ১৮৪৯ সালের ২২ জানুয়ারি সুইডেনের স্টকহোমে জন্মগ্রহণ করা এ মানুষটি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে তিনি নাট্যকার, গল্পকার, চিত্রকর, ঔপন্যাসিক এবং কবি। চার দশকেরও বেশি সময়জুড়ে সুইডিশ সাহিত্যাঙ্গন দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। আজও তাঁর সৃষ্টিকর্ম তাঁর সময়ের মতই প্রাণবন্ত এবং যুগোপযোগী। দাপিয়ে বেড়ানো’ কথাটা আক্ষরিক অর্থেই স্ট্রিনডবার্গের সঙ্গে ভীষণভাবে মানানসই। কারণ, প্রচলিত বিশ্বাস আর ধ্যানধারণাকে তিনি অনবরত আঘাত করেছেন তাঁর কলম আর তুলির আঁচড়ে। ব্যক্তিজীবনেও ছিলেন একগুঁয়েরকম স্বাধীনচেতা। নিজেকে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচারী ঘোষণা করে তিনি বলতেন–“জীবনের জটিলতার জালে আমরা এত বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়েছি যে, এ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে, সুন্দর করে শুরু করতে হবে।” এ অনুভূতি থেকেই হয়তো জীবনব্যাপী সাহিত্যকর্ম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। গল্প, নাটক আর কবিতার বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন সময়ে ভিন্নতর আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। তবে, তিনি সব সময়ই ‘প্রাকৃতিক নিয়ম’(Natural Law) কথাটায় বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন, আরোপিত কোন মতামত বা বক্তব্য কখনোই মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। একে উল্লেখ করেছেন ‘বৃহত্তর প্রাকৃতিকতাবাদ’ (Greater Naturalism) হিসেবে। নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করতেন, কিন্তু সে সমতার অর্থ এই নয় যে, নারী-পুরুষকে একই কাজ করতে হবে। নারী-পুরুষের মিলন নিয়েও প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর। “দৈহিক মিলন কখনোই ‘কাম-নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়, বরং, মানব মনের সুকুমার প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।” স্ট্রিনবার্গ আরোপিত নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন না। ফলে, তথাকথিত নারী আন্দোলন’ বা ‘নারী অধিকার’ শব্দগুলোর প্রতি ভীষণ বিরক্ত ছিলেন। উপরন্তু, এগুলোকে মানবজাতির মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টিকারী মতবাদ মনে করতেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই যথাযোগ্য মর্যাদা পাওয়া উচিত বলে বিশ্বাস করতেন। এ বিশ্বাস থেকেই, ১৮৮৪ সালে সুইডিশ নারীদের ভোটাধিকার আদায়ে তিনি রীতিমত আন্দোলন করেছেন। অনেক সমালোচক স্ট্রিনবার্গকে ‘নারী-বিদ্বেষী’ বলে রায় দিলেও বাস্তবতার নিরিখে একে খারিজ করে দেওয়াই সমীচীন। কারণ, যে সময়ে তিনি নারীদের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্বেষ প্রদর্শন করেছেন সে সময়ে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিলেন। অথচ তাঁর বিখ্যাত কাজগুলোর প্রায় সবই ঐ ভারসাম্যহীনতার আগে করা। সর্বোপরি, ‘নিরপেক্ষ অবস্থান বলে কিছু হয় না। লেখকের বক্তব্যকে কালের কষ্টিতে যাচাই করে নেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের ওপর বর্তায়।
স্ট্রিনডবার্গের বক্তব্যে ছিল ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছু বলাকে কখনোই বরদাস্ত করতে পারতেন না। ফলে, নরওয়ের বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের বর্ণনাবহুল নাটকগুলোকে ভীষণ অপছন্দ করতেন, সেগুলোর বিষয়বস্তু নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। এ-নিয়ে দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়েও শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল–একে-অন্যকে খোঁচা দিলে বেশকিছু লেখালেখি করেছেন। তবে, স্ট্রিনবার্গের অনুসারীর সংখ্যাও কিন্তু নেহাত কম নয়। টেনিস উইলিয়ামস, এডওয়ার্ড অ্যালবি, ম্যাক্সিম গোর্কি, জন অসবর্নসহ অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক নিজেদের লেখালেখিতে স্ট্রিনবার্গের প্রভাব স্বীকার করেছেন। আমেরিকান নাট্যকার ইউজিন ও’নিল ১৯৩৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর স্ট্রিনডবার্গকে নিজের অনুপ্রেরণা হিসেবে স্বীকার করে তাঁকে ‘সবচাইতে প্রতিভাধর আধুনিক নাট্যকার’ (The greatest genius of all modern dramatists) হিসেবে আখ্যায়িত করেন। যদিও তার বহু আগেই স্টিনডবার্গ চলে গেছেন না-ফেরার দেশে। ১৯১১-তে নিউমোনিয়ায়। আক্রান্ত হন। সেরে ওঠার আগেই ‘কোলন ক্যান্সার’ ধরা পড়ে। বেশ কয়েক মাস শয্যাশায়ী থেকে ১৯১২ সালের ১৪ মে স্ট্রিনবার্গ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
সুইডিশ সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্য আজও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।
রোমিও অ্যান্ড জুলিয়া
এক সন্ধ্যায় গানের স্বরলিপি হাতে বাড়ি ফিরে উচ্ছ্বসিত স্বামী তাঁর স্ত্রীকে বললেন,
–চল আজ রাতের খাবারের পর আমরা গান করি!
–হুম! তা না-হয় হল; কিন্তু তোমার হাতে ওটা কী?
স্বামী গর্বের সাথে ঘোষণা করলেন,
–‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়া’র পিয়ানো ভার্সন। চেনো এটা?
–“অবশ্যই! কিন্তু কাউকে কখনো বাজাতে শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।”
স্বামী এবারে আরও উচ্ছ্বসিত হলেন–“ওহহহ! তুমি জানো না কী অসাধারণ এটা! এক সময় এটা ছিল আমার স্বপ্নের মত, আমার ঘোরের মত। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো, আমি মাত্র একবারই এটা শুনেছি, তাও প্রায় কুড়ি বছর আগে।
রাতের খাবারের পর বাচ্চাদের ঘুমাতে পাঠানো হল। পুরো বাড়িতে একরকম নিস্তব্ধতা নেমে এল। এর মাঝেই পিয়ানোর ওপর এক চিলতে আলো দেখা গেল। লিথোগ্রাফের কাগজে ছাপানো শিরোনামে চোখ বোলালেন স্বামী,
–‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়া! গাউনড এর সেরা সৃষ্টি। এটা গাওয়া আমাদের জন্য খুব মুশকিল হবে বলে মনে হয় না।
স্বামী গলা খাকারি দিলেন, আর স্ত্রী উচ্চগ্রাম থেকে বাজাতে শুরু করলেন। ডি মেজর’ থেকে গাওয়া শুরু হল।
–“ওয়াও! অসাধারণ! তাই না?” স্বামীর চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক।
–“হুম, হবে হয়তো!” স্ত্রীকে খুব একটা উচ্ছ্বসিত মনে হল না।
–এখন কিন্তু যুদ্ধের বাজনা বাজাতে হবে! এই অংশটুকুর কোন তুলনাই হয় না। আমার মনে আছে, রয়েল থিয়েটারে একটা কোরাসে এটা শুনেছিলাম।
পিয়ানোতে এবার যুদ্ধংদেহী আওয়াজ বাজল।
–“বলেছিলাম না! এখানে যুদ্ধের মার্চ বাজবে।” স্বামী এমনভাবে বলছেন যেন ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়া তিনি নিজেই লিখেছেন!
–“জানি না!” স্ত্রীর খাপছাড়া উত্তর। “আমার কাছে তো নিছক পিতলের ঝনঝনানি মনে হচ্ছে!”
স্বামী বেচারা এখনো সুরের তালে মগ্ন আছেন। চতুর্থ দৃশ্যে অপেরা অংশটা শুনতে কেমন লাগবে তা-নিয়ে ভাবছেন। দীর্ঘক্ষণ পর অপেরার অংশ পাওয়া গেল।
–এইতো, এইতো এখানে অপেরা বাজবে।
বড় করে দম নিয়ে তিনি অপেরায় গলা মেলালেন। ট্র্যাম, ট্রাম, ট্রা ট্যাম-ট্যা ট্র্যাম, ট্রাম বেজ বাজতে থাকলো।
বাজনা শেষ হবার পর স্ত্রী মন খারাপ করে বললেন, “কিছু মনে না করলে একটা কথা বলবো? আমার কিন্তু এটাকে খুব বিশেষ কিছু মনে হল না।” এইবেলা স্বামী হতাশ হলেন। স্বীকার করতেই হল, বাজনা শুনে তাঁর নিজের কাছেও ফাঁপা কলসির আওয়াজের মত মনে হয়েছে।
–“বাজানোর সময়ই আমি বুঝেছি” স্ত্রীর সরল স্বীকারোক্তি। “সত্যি বলতে কি, এগুলোকে বেশ পুরনো মনে হল!”
–“ভাবতে অবাক লাগছে, এর মধ্যেই গাউন্ড পুরনো হয়ে গেল!” স্বামীও সহমত পোষণ করলেন। তারপর, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন, “তুমি কি আর কিছুক্ষণ বাজাতে পারো?” পরক্ষণেই তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: “তারচেয়ে বরং চল তিন তালের ‘ক্যাতিনা বাজানো যাক। মনে আছে? উহ! উঁচু স্কেলের অংশটুকু একেবারে যেন স্বর্গীয়!”
কিন্তু এবারে বাজনা শেষ হবার পর স্বামীকে আগের চেয়েও বেশি বিষণ্ণ মনে হল। স্বরলিপিগুলো একপাশে সরিয়ে রাখলেন তিনি, যেন এভাবে অতীতের দরজাকে বন্ধ করতে চাচ্ছেন। “চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক”, বিমর্ষ স্বামীর প্রস্তাব। দুজন দুটো চেয়ার টেনে টেবিলের পাশে বসে বিয়ার খেতে লাগলেন।
কিছুক্ষণ পর স্বামী প্রথম মৌনতা ভঙ্গ করলেন।
–“মানতে কষ্ট হচ্ছে, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। এতক্ষণ যেন আমরা ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়া’র সঙ্গে পাল্লা দিলাম, কে আগে বুড়িয়ে যেতে পারি! কুড়ি বছর আগে প্রথম শুনেছিলাম। তখন আমি টগবগে যুবক। চারপাশে কত বন্ধুবান্ধব ছিল, কত হাসি-আনন্দ-উচ্ছ্বাস। ঠোঁটের ওপর সে-বার প্রথম গোঁফের রেখা দেখা দিল, কলেজের নতুন ক্যাপ মাথায় কী গর্ব হচ্ছিল আমার! মনে হয় যেন, এইতো সেদিন–ফ্রীড, ফিল আর আমি মিলে অপেরায় গেলাম। তার মাত্র কিছুদিন আগে আমরা ‘ফস্ট’ শুনেছিলাম, আর সেবার ‘গাউন্ড’ শুনেতো রীতিমত ভক্ত বনে গেলাম। কিন্তু রোমিও আমাদের সব প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেল। এক বুনো উদ্দামতা যেন গ্রাস করেছিল আমাদের! আর এখন…?” স্বামীর বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।
“ওরা দুজনেই এখন মৃত। মারা যাবার সময় ফ্রিড ছিল প্রাইভেট সেক্রেটারি। খুব উচ্চাভিলাষী ছিল। ফিল ছিল মেডিকেলের ছাত্র। আর হতভাগ্য আমি! স্বপ্ন দেখেছিলাম মন্ত্রী হবার, অথচ এখন রেজিমেন্টের বিচারকগিরি করি। সময় যে কত দ্রুত বয়ে চলে, চোখেই পড়ে না। তবে আমার চোখের নিচের কালি যে আরও গম্ভীর হয়েছে, কানের পাশের চুলে যে পাক ধরেছে, তা কিন্তু বেশ ভালোভাবেই চোখে পড়ে! কবরের দিকে এতটা পথ পাড়ি দিয়েছি কখনো লক্ষই করিনি।”
–হুম! আসলেই তাই। আমরা বুড়িয়ে গেছি। আমাদের সন্তানদের দেখেই সেটা বোঝা যায়। তোমার লক্ষণগুলো যে আমার মধ্যেও দেখা দিয়েছে, তা নিশ্চয় খেয়াল করেছ? তুমি অবশ্য সব সময়ই এসব এড়িয়ে যেতে চাও।
–না-না ওভাবে বলো না।
–“এটাই যে সত্যি, কী করব বলো? আমি খুব ভালোভাবেই জানি, আমার সৌন্দর্য হারিয়ে যাচ্ছে, চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে; খুব শীঘ্রই হয়তো সামনের দাঁতও পড়ে যাবে।” স্ত্রীর এমন বিষণ্ণতার মাঝে স্বামী একটু বাধা দিলেন,
–চিন্তা করে দেখ, সবকিছু কেমন দ্রুত বয়ে যায়। আমার কী মনে হয় জানো? ইদানীং মানুষগুলো খুব দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছে, আগে এমনটা হত না। বাবার বাড়িতে দেখেছি, হরহামেশা ‘হেইডেন’ আর ‘মোজার্ট’ বাজানোনা হত, অথচ বাবার জন্মেরও বহু আগে এরা মারা গেছেন। আর এখন দেখ! এই ক’দিনেই গাউন্ড সেকেলে হয়ে গেল! ছেলেবেলার পছন্দগুলোকে পুরনো হয়ে যেতে দেখা যে কত কষ্টের, বলে বোঝানো যাবে না। তার চেয়েও বেশি কষ্ট হয় যখন মনে হয়, আমি নিজেই পুরনো হয়ে যাচ্ছি।”
কথাগুলো বলে, স্বামী একবার একটু দাঁড়িয়ে আবার পিয়ানোতে বসলেন। স্বরলিপিটা হাতে নিয়ে এমনভাবে পাতা ওল্টাতে থাকলেন যেন টেবিলের ড্রয়ারে সযত্নে রাখা কোন প্রিয় জিনিস, প্রিয়জনের একগোছা চুল, শুকিয়ে যাওয়া ফুল কিংবা সুতোর কাঠিম খুঁজছেন। স্বরলিপির কাগজটার কালো অক্ষরগুলো তাঁর দুচোখ আটকে দিল–ওগুলো যেন অক্ষর নয়, যেন কতগুলো ছোট্ট পাখি দোল খাচ্ছে! কিন্তু বসন্তের গান কেন শোনা যাচ্ছে না? সেই তারুণ্যের উদ্বেলতা, ভালবাসার গোলাপ ফোঁটা গান, কোথায় হারিয়ে গেল?
হঠাৎ করেই অক্ষরগুলো যেন ঝাপসা হয়ে এল–খুব অদ্ভুত, অপরিচিত ঠেকলো ওদের। যেন জীবন-বসন্তের সাজানো বাগান আগাছায় ছেয়ে গেল! হ্যাঁ, তাই-ই হয়েছে–পিয়ানোর গায়ে ধূলো জমেছে, কাঠের বোর্ড শুকিয়ে গেছে, আর স্বামী-স্ত্রীর অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে। সমস্ত রুমটায় একটা দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনিত হল। শূন্য-হৃদয় নিংড়ানো ভীষণ ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস, একটা ভীষণ নীরবতা আচ্ছন্ন করল রুমটাকে।
-”তবুও সবকিছুই এক! কী অদ্ভুত!” কী মনে করে যেন, স্বামী হঠাৎ করেই কথাগুলো বলে উঠলেন। “আমাদের গানে, আমাদের বাজনায় সেই ‘ভূমিকা’র অংশটুকু করা হয়নি। আমার স্পষ্ট মনে আছ, হার্প আর কোরাসের সাথে চমৎকার একটা ভূমিকা’র অংশও ছিল। সুরটা অনেকটা এরকম…” গুনগুন করে সুর ভাজলেন তিনি। মনে হচ্ছে, যেন কোন সংকীর্ণ উপত্যকা বেয়ে শীর্ণ এক নদীর ধারা নেমে আসছে। নোটের পরে নোট আসছে ঠোঁটের কিনারায়। ধীরে-ধীরে সেই নোট বেয়ে এক চিলতে হাসির রেখাও উঁকি দিয়ে গেল। স্বামীর চেহারার আচ্ছন্নতা উধাও হতে থাকল। পিয়ানোতে হাত লাগলো তাঁর। সেই হাতের ছোঁয়ায়, যত্নে-বেড়ে ওঠা প্রাণবন্ত তারুণ্য যেন সুরের খাঁদ থেকে উঠে এসে পিয়ানোর বুকে ভালোবাসার বান জাগালো। বেশ জোরালো গলায় তিনি বেজ এর অংশটুকু গাইলেন।
স্ত্রীও এবারে কষ্ট-কল্পনার রাজ্য থেকে নেমে এলেন। কান্না-ভেজানো চোখে তন্ময় হয়ে কিছুক্ষণ স্বামীর গান শুনলেন। তারপর, চোখ-ভরা আনন্দাশ্রু নিয়ে ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন–কী গাইছ তুমি?
–কেন ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়া’। আমাদের রোমিও অ্যান্ড জুলিয়া।
স্বামীর ওপর হঠাৎ যেন কিছু একটা ভর করল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্বরলিপিটাকে স্ত্রীর দিকে ঠেলে দিলেন,
–দেখ! এই দেখ, এই রোমিও আমাদের বাবা-দাদার, এই রোমিও আমাদেরও! পড়ে দেখ, এই আমাদের বেলিনি। ওহ, আমরা আসলে অতটা বুড়িয়ে যাইনি!
স্ত্রী তাঁর স্বামীর ঘন-চকচকে চুলের দিকে তাকালেন। দেখলেন স্বামীর জ্বলজ্বলে চোখ আর দৃপ্ত ভুরু। তাঁর মনের কোণে কোথায় যেন একটু হাওয়া লাগলো।
–“তুমি! তোমাকেও এক অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী মনে হচ্ছে!” স্বামীর বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। “বুড়ো বেলিনিকে দেখে আমরা নিজেরাও ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলাম। আসলে কিন্তু আমরা অতটা বুড়ো হইনি। আমার আগেই কিছুটা সন্দেহ হয়েছিল।”
–“উঁহু! আমি আগে সন্দেহ করেছি” ঠোঁট উল্টে স্ত্রীর প্রতিবাদ।
–হতেই পারে! তোমার বয়স তো আমার চেয়ে কম।
–না-না-না, তুমিই আগে সন্দেহ করেছ….
আর এভাবেই, স্বামী-স্ত্রী একজোড়া নিষ্পাপ শিশুর মত নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করতে লাগলেন–“দুজনের মধ্যে কে বড়?” এই প্রশ্ন নিয়ে। তাদের দেখে বোঝার উপায় নেই, কীভাবে কিছুক্ষণ আগেও তাঁরা ‘বুড়িয়ে যাওয়া নিয়ে আফসোস করে কাঁচা চুল পাকিয়ে ফেলছিলেন!