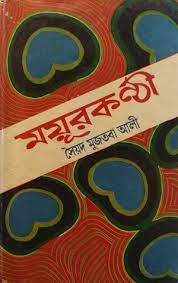- বইয়ের নামঃ ময়ূরকণ্ঠী
- লেখকের নামঃ সৈয়দ মুজতবা আলী
- প্রকাশনাঃ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
- বিভাগসমূহঃ প্রবন্ধ
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ইস্কুলে পড়ি; ষোল বছর বয়স। বিশ্বাস হয়, বিশ্ববিখ্যাত অবনীন্দ্রনাথ তাকে প্রথম দর্শনেই পূর্ণ দু ঘণ্টা ধরে ভারতীয় কলার নবজাগরণের ইতিহাস শোনালেন?
সত্যিই তাই হয়েছিল। আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তিন মিনিট যেতে না যেতেই তিনি হঠাৎ সোৎসাহে এক ঝটিকায় হেলান ছেড়ে খাড়া হয়ে বসে আমাকে সেই প্রাচীন যুগের কথা—কি করে তিনি ছবি আঁকা শিখতে আরম্ভ করলেন, সে ছবি দেখে দ্বিজেন্দ্ৰনাথ কি বললেন, হ্যাভেলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ, টাইকনের সঙ্গে তার সহযোগ, ওরিয়েন্টাল সোসাইটির গোড়াপত্তন, নন্দলাল অসিতকুমারের শিষ্যত্ব, আরো কত কী যে বলে গেলেন তার অর্ধেক লিখে রাখলেও আজ একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর কলা-ইতিহাস হয়ে যেত।
আর কী ভাষা, কী রঙ। আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন মনে মনে দেখি, সেদিন অবনীন্দ্ৰনাথ কথা বলেন নি, সেদিন যেন তিনি আমার সামনে ছবি এঁকেছিলেন। রঙের পর রঙ চাপাচ্ছেন; আকাশে আকাশে মেঘে মেঘে। সূর্যস্ত সূর্যোদয়ের যত রঙ থাকে তার থেকে তুলে নিয়ে ছবির এখানে লাগাচ্ছেন, ওখানে লাগাচ্ছেন আর যতই ভাবি এর পর আর নতুন নতুন রঙ বানিয়ে ছবির উপর চাপাচ্ছেন।
তার কী উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তার সুখদুঃখ, তার পতন-অভু্যদয়ের অনুভূতি অজানা অচেনা এক আড়াই ফোটা ছোকরার মনের ভিতর সঞ্চালন করার প্রচেষ্টা। বুঝলুম, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভালোবেসেছেন ভারতীয় কলাশিল্পকে আর আপনি বুকের পাঁজর জুলিয়ে নিয়ে’ প্ৰদীপ্ত করে দিয়েছেন আমাদের দেশের নির্বাপিত কলাপ্রচেষ্টার অন্ধ-প্ৰদীপ।
***
তারপর একদিন তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানেও আমি কেউ নই। রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল এবং নন্দলালের কৃতী শিষ্যগণ তাঁর চতুর্দিকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, বিশ্বকবিরূপে, শান্তিনিকেতনে আচার্যরূপে। আর সেদিন রবীন্দ্ৰনাথ যে ভাষা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আসন নিতে অনুরোধ করলেন সে রকম ভাষা আমি রবীন্দ্রনাথের মুখে তার পূর্বে কিংবা পরে কখনো শুনি নি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেন গদ্যে গান গেয়েছিলেন, আমার মনে হয়, সেই দিন তিনি প্রথম গদ্য কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন। দেশেবিদেশে বহু সাহিত্যিককে বক্তৃতা দিতে শুনেছি, কিন্তু এরকম ভাষা আমি কোথাও শুনি নি-আমার মনে হয়, দেবদূতরা স্বর্গে এই ভাষায় কথা বলেন-সেদিন যেন ইন্দ্রপুরীর একখানা বাতায়ন খুলে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উর্বশীর বীণা গুঞ্জরণ করে উঠেছিল।
***
অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তরায়ণের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি-অবনীন্দ্ৰনাথ সদলবলে আসছেন। আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে বড় আনন্দ হল।
তখন আমাদের সবাইকে বললেন, ‘জানো, বৈজ্ঞানিকরা বড় ভীষণ লোক–আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে দেয়। এই দেখো না, আজ সন্ধ্যায়। আমি দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো কালো মেঘ এসে বাসা বঁধছে ভুবনাডাঙার ওপারে ডাক-বাঙলোর পিছনে। মেঘগুলোর সর্বাঙ্গে কেমন যেন ক্লান্তির ভাব আর বাসা বাঁধতে পেরে তারা একে অন্যকে আনন্দে আলিঙ্গন করছে।
রাখী শুনে বলেন, ‘মেঘ কোথায়? এ তো ধানকলের ধোঁয়া!’
এক লহমায় আমার সব রঙীন স্বপ্ন বরবাদ হয়ে গেল। তাই বলছিলুম। বৈজ্ঞানিকগুলো ভীষণ লোক হয়।’*
সে-যাত্রায় যে কদিন ছিলেন তিনি যে কত গল্প বলেছিলেন, তরুণ শিল্পীদের কত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তার ইতিহাস, আশা করি একদিন সেই শিল্পীদের একজন লিখে দিয়ে আমাদের প্রশংসাভাজন হবেন।
***
আবার সেই প্রথম দিনের পরিচয়ে ফিরে যাই।
আমি তখন অটোগ্রাফ শিকারে মত্ত। প্রথম গগনেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলুম। আমার অটোগ্রাফে কিছু একে দিতে। তার কাছে রঙ তুলি তৈরি ছিল। চট করে পাঁচ মিনিটের ভিতর আকাশে ঘন মেঘ। আর তার ফাঁকে ফাঁকে গুটি কয়েক পাখি এঁকে দিলেন।
এর কয়েক দিন পূর্বে শাস্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা কলকাতায় এসে ‘বর্ষামঙ্গল’ করে গিয়েছে। গগনেন্দ্ৰনাথ ছবি এঁকে দিয়ে বললেন, ‘পাখিরা বর্ষামঙ্গল করছে।’
অবনীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে তিনি বললেন, ‘তুমি নিজে ছবি আঁকো না কেন?’
আমি সবিনয়ে বললুম, ‘আমি ছবি দেখতে ভালোবাসি।’
বললেন, ‘দাও তোমার অটোগ্রাফ। তোমাকে কিছু একটা লিখে দিচ্ছি। আর যেদিন তুমি তোমার.প্রথম আঁকা ছবি এনে দেখাবে সেদিন তোমার বইয়ে ছবি এঁকে দেব।’
বলে লিখলেন, ‘ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে স্থলে প্রতিমুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো।
‘আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও, তবে আসন গ্ৰহণ করো এক জায়গায়, দিতে থাকো রঙের টান, তুলির পৌঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্ৰষ্টার আনন্দ’।*
——
* পাঠক, অবনীন্দ্ৰ যে ভাষায় বলেছিলেন তার সন্ধান এতে পাবেন না।
আচার্য তুচ্চি
দিল্লির ইন্ডিয়ান কালচারেল এসোসিয়েশন গত শুক্রবার দিন ইতালির খ্যাতনামা অধ্যাপক জিয়োসেপ্নে তুচ্চিকে এক সভায় নিমন্ত্রণ করে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সভাস্থলে ইতালির রাজদূত ও শ্ৰীযুক্তা তুচ্চিও উপস্থিত ছিলেন।
ভারত-তিব্বত-চীনের ইতিহাস এবং বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ এবং দেশদেশান্তরে তার প্রসার সম্বন্ধে আজকের দিনে অধ্যাপক তুচ্চির যে জ্ঞান আছে তার সঙ্গে বোধ হয়। আর কারোর তুলনা করা যায় না। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে সব শাস্ত্র সংস্কৃতে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তিব্বতী এবং চীনা অনুবাদে এখানে পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে অধ্যাপক তুচ্চি নানাপ্রকারের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস নির্মাণ করে যাচ্ছেন, সে ইতিহাস ভারতের গৌরব বর্ধন করে চলেছে। ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু অনুমান করি, প্রায় পয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি এই কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য এখনো অটুট, তাই আশা করা যেতে পারে তিনি আরো বহু বৎসর ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যার সেবা করতে পারবেন।
***
ইতালির স্কুলে থাকতেই তুচ্চি সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। কলেজে ঢোকার পূর্বেই তাঁর মহাভারত, রামায়ণ ও কালিদাসের প্রায় সব কিছুই পড়া হয়ে গিয়েছিল-টোলে না। পড়ে এতখানি সংস্কৃত চর্চা এই ভারতেরই কটি ছেলে করতে পেরেছে? কলেজে তুচ্চি সংস্কৃতের বিখ্যাত অধ্যাপক ফরমিকির সংস্রবে। আসেন। অধ্যাপক ফরমিকির নাম এদেশে সুপরিচিত নয়, কিন্তু ইতালির পণ্ডিত মাত্রই জানেন, সে দেশে সংস্কৃত চর্চার পত্তন ও প্রসারের জন্য তিনি কতখানি দায়ী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তার ছিল অবিচল অনুরাগ এবং গভীর নিষ্ঠা। অধ্যাপক তুচ্চি তার অন্যতম সার্থক শিষ্য।
***
অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিৎস ও লেসনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে স্বদেশে চলে যাওয়ার পর এদেশ থেকে রবীন্দ্ৰনাথ নিমন্ত্রণ করেন অধ্যাপক ফরমিকি এবং তুচ্চিকে। ১৯২৫-এ এরা দুজন ভারতবর্ষে আসেন। ‘
অধ্যাপক ফরমিকি শাস্তিনিকেতনে সংস্কৃত পড়বার সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, ‘জানো সমস্ত জীবনটা কাটল ছাত্রদের সংস্কৃত ধাতুরূপ আর শব্দরূপ শিখিয়ে। রাসিয়ে রসিয়ে কাব্যনাট্য পড়ানো আরম্ভ করার পূর্বেই তাদের কোর্স শেষ হয়ে যায়–তারা তখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ করে দেয়। জীবনে এই প্রথম শাস্তিনিকেতনে সুযোগ পেলুম পরিণত-জ্ঞান ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাব্যনাট্য পড়ার। ব্যাকরণ পড়াতে হচ্ছে না, এটা কি কম আরামের কথা।’
এবং আশ্চর্য, আমার মত মুখদ্দেরও তিনি অবহেলা করতেন না। এবং ততোধিক আশ্চৰ্য্য ক্ষমতা ছিল তার-কঠিন জিনিস সরল করে বোঝাবার। সাংখ্য বেদান্ত তখনো জানতুম না, এখনো জানি নে, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে বসুমতী বেহনের বাড়ির বারান্দায় মোড়াতে বসে সাংখ্য এবং বেদাস্তের প্রধান পার্থক্য তিনি কি অদ্ভুত সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলেছিলেন। তিতিক্ষু পাঠক অপরাধ নেবেন না, যদি আজ এই নিয়ে গর্ব করি যে অধ্যাপক ফরমিকি আমাকে একটুখানি মেহের চোখে দেখতেন। রাস্তায় দেখা হলেই সাংখ্য বেদান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বাজিয়ে নিতেন, যা শিখিয়েছেন আমার ঠিক ঠিক মনে আছে কি না।
হেমলেট চরিত্রের সাইকো-এনালেসিস ইয়োরোপে তিনিই করেন। প্রথম। হেমলেট যে কেন প্রতিবারে তার কাকাকে খুন করতে গিয়ে পিছুপা হত সে কথা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।
***
গুরু পড়াতেন সংস্কৃত আর শিষ্য পড়াতেন ইতালিয়ান। অধ্যাপক তুচ্চির অন্যতম মহৎ গুণ, তিনি ছাত্রের মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে অধ্যাপনা করেন। আমরা একটুখানি ইতালিয়ান শিখে নিয়ে বললুম, এইবারে আমরা দানুনন্দজিয়ো পড়ব।
তুচ্চি বললেন, ‘উপস্থিত মাদ্ৰজিনি পড়ো।’
তারপর বুঝিয়ে বললেন, ‘তোমরা এখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। তোমাদের চিস্তাজগতে এখন স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতা সংগ্রাম কাকে বলে এই নিয়ে তোলপাড় চলছে। আর এসব বিশ্লেষণ মাদজিনি যে রকম করে গিয়েছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে তিনি যেরকম উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন এ রকম আর কেউ কখনো পারেননি। তোমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এগুলো মিলে যাবে, ভাষা শেখাটাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে।’ হলও তাই। অধ্যাপক তুচ্চি শাস্তসমাহিত গভীর প্রকৃতির পণ্ডিত নন-ৰ্তার ধাঁচ অনেকটা ফরাসিস। অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে যান। আর মাদজিনির ভুবন-বিখ্যাত বক্তৃতাগুলোতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রচুরতম খোরাক রয়েছে তা যাঁরা মাদজিনি পড়েছেন র্তারাই জানেন—এমন কি এই গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ও চাৰ্চিল মাদজিনির বক্তৃতা আপন বক্তৃতায় কাজে লাগিয়েছেন। তুচ্চি পড়াতে পড়াতে উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠতেন আর
‘আভান্তি, আভাস্তি ও ফ্রাতেল্লি।’
‘অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, হে ভ্ৰাতৃবৃন্দ–’
‘আসবে সে দিন আসবে, যেদিন নবজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তোমরা পিছন পানে তাকাবে-পিছনের সব কিছু তখন এক দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে, তার কোনো রহস্যই তোমাদের কাছে তখন আর গোপন রইবে না; যেসব দুঃখবেদনা তোমরা একসঙ্গে সয়েছ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তোমরা তখন আনন্দের হাসি হাসবে।’
এসব সাহসের বাণী সর্বমানবের সুপরিচিত। আমরা যে উৎসাহিত হয়েছিলুম তাতে আর বিচিত্র কি?
***
তারপর দীর্ঘ সাতাশ বৎসর কেটে গিয়েছে। এর ভিতর অধ্যাপক তুচ্চি পাণ্ডুলিপির সন্ধানে ভারত-তিব্বত বহুবার ঘুরে গিয়েছেন এবং তাঁর পরিশ্রমের ফল ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার এবং ইতালির সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।
ইতালির প্রাচ্যবিদ্যামন্দির আচার্য তুর্চ্চির নিজের হাতে গড়া বললে অত্যুক্তি করা হয় না। শুধু যে সেখানে সংস্কৃত, পালির চর্চা হয় তাই নয়, বাঙলা, হিন্দি শেখাবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে, এবং চীনা, জাপানী, তিব্বতী ভাষার অনুসন্ধান করে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেখানে লেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তুচ্চি নিজে যে সব প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যে সব সারগর্ভ পুস্তক রচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ তালিকা দিতে গেলেই এ গ্রন্থের আরো দু’পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে।
***
সম্বর্ধনা-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আচার্য তুচ্চি বলেন, ‘বহু প্ৰাচীনকাল থেকে ভারতইতালিতে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত ছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন (দক্ষিণ-ভারতে আজও প্রতি বৎসর বহু রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়), কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। ভারত-ইতালির আত্মায় আত্মায় যে ভাব বিনিময় হয়েছিল। সেইটেই সবচেয়ে মহান তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বানুসন্ধান করে নূতন করে আমাদের ভাবের লেনদেন, আদানপ্রদান করতে হবে। ‘আমি ইতালিতে যে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছি। সেটিকে সফল করবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।’
***
আমরা একবাক্যে বলি ভগবান আচার্য তুচ্চিকে জয়যুক্ত করুন।
আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত
কদম কদমা বঢ়ায়ে জা এগিয়ে যা এগিয়ে যা,
খুশিকে গীত্ব গায়ে জা খুশির গীত গাইতে যা।
ইয়েহ জিন্দগী হ্যায় কৌম কী দেশের তরে জীবন ধন
(তো) কৌম পৈ লুটায়ে জা।। দেশের লাগি করবি নে পণ?
তু শেরে হিন্দ আগে বঢ় শেরে হিন্দ এগিয়ে যা।
মরণেসে ফিরভি তু ন ডর সামনে মরণ ফিরে না চা।।
আসমান তক্ উঠায়ে শির আকাশ বিধে তুলবি শির
জোশে ওতন বঢ়ায়ে জা।। দেশের জোশ বাড়বে বীর।
তেরে হিম্মৎ বঢ়তী রহে বাড়ুক বাড়ুক সাহস তোর
খুদা তেরী সুনন্ত রহে খুদা তোরে দেবেন। জোর।
জো সামনে তেরে চঢ়ে সামনে বাধা পরোয়া না কর
(তো) খাকমে মিলায়ে জায়।। ধুলায় তারা পাবে যে গোর।।
চলো দিল্লী পুকারকে হুঙ্কারিয়া দিল্লী চল
কোমী নিসান সম্ভালকে কৌমী নিশান জাগিয়ে তোল
লাল কিল্লে গাঢ়কে লালকেল্লায় ঝাণ্ডা খোল
লহ রায়ে জা লহ রায়ে জা।। এগিয়ে যা ফুর্তিতে চল।।
কদম কদমা বঢ়ায়ে জা।। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা।।
———–
শেরে হিন্দ = হিন্দুস্থানের ব্যাঘ্র, জোশ্ = শক্তি, কৌমী নিশান = জাতীয় পতাকা।
আমরা হাসি কেন?
প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কবিগুরু বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভায় এক খ্যাতনামা লেখকের সদ্যপ্রকাশিত একটা রচনা পাঠ করেন। রচনার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, ‘আমরা হাসি কেন’?
এতদিন বাদে আজ আর সব কথা মনে নেই, তবে এইটুকু স্পষ্ট স্মরণে পড়ছে যে, বের্গসন হাসির কারণ অনুসন্ধান করে যে সব তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেছিলেন, প্ৰবন্ধটি মোটের উপর তারই উপর খাড়া ছিল।
প্ৰবন্ধ পাঠের পর রবীন্দ্ৰনাথ আপনি বক্তব্য বলেন।
সভায় উপস্থিত অন্যান্য গুণীরাও তখন নানারকম মতামত দেন এবং সবাই মিলে প্রাণপণ অনুসন্ধান করেন, ‘আমরা হাসি কেন?’ যতদূর মনে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পাকাপাকি কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।
পরদিন আচাৰ্য ক্ষিতিমোহন সেন সবার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ‘হাসির কারণ বের করতে গিয়ে সকলের চোখের জল বেরিয়ে গিয়েছিল।’ (ঠিক কি ভাষায় তিনি জিনিসটি রাসিয়ে বলেছিলেন আজ আর আমার সম্পূর্ণ মনে নেই-আশা করি আচার্য অপরাধ নেবেন না)।
***
দিল্লির ফরাসিস ক্লাবের (সের্কল ফ্রাসেঁ’ অর্থাৎ ‘ফরাসি-চক্ৰ’) এক বিশেষ সভায় মসিয়ে মার্তে নামক এক ফরাসি গুণী গত বুধবার দিন ঐ একই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ ‘আমরা হাসি কেন?’ একখানি প্ৰমাণিক প্ৰবন্ধ পাঠ করেন।
ফরাসি রাজদূত এবং আরো মেলা ফরাসি-জাননেওয়ালা ফরাসি অ-ফরাসি ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফরাসি কামিনীগণ সর্বদাই অত্যুত্তম সুগন্ধ ব্যবহার করেন বলে ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল। আমি বুঝি প্যারিসে বসে আছি।
(এ কিছু নূতন কথা নয়—এক পূর্ববঙ্গবাসী শিয়ালদা স্টেশনে নেমেও গেয়েছিলেন,-
ল্যামা ইস্টিশানে গাড়ির থনে
মনে মনে আমেজ করি
আইলাম বুঝি আলী-মিয়ার রঙমহলে
ঢাহা জেলায় বশ্যাল ছাড়ি।)
শুধু প্যারিস নয়। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন ‘কোতি’, ‘উবিগাঁর’ কুশবায়ের দোকানে বসে আছি।
ডাঃ কেসকর উত্তম ফরাসি বলতে পারেন। তিনি সভাপতির আসন গ্ৰহণ করে প্ৰাঞ্জল ফরাসিতে বক্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।
বের্গসন আর সেই চিরন্তন কারণানুসন্ধান, ‘হাসি কেন?? আমি তো নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেলুম-ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে রকমধারা হয়েছিলুম-কিন্তু তবু কোনো হদিস মিলল না।
কিন্তু সেইটো আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই দিল্লিশহর যে ক্ৰমে ক্ৰমে আন্তর্জাতিক মহানগরী হতে চলল। সেইটেই বড় আনন্দের কথা।
এতদিন ধরে আমরা ইয়োরোপকে চিনতে শিখলুম ইংরেজের মাধ্যমে এবং তাতে করে মাঝে মাঝে আমরা যে মারাত্মক মার খেয়েছি, তার হিসেবা-নিকেশ এখনো আরম্ভ হয়। নি। একটা সামান্য উদাহরণ নিন।
ইংরেজের আইরিশ সন্টু, মাটন রাস্ট আর প্লামপুডিং খেয়ে খেয়ে আমরা ভেবেছি ইয়োরোপবাসী মাত্রই বুঝি আহারাদি বাবতে একদম হটেনটট। তারপর যেদিন উত্তম ফরাসি রান্না খেলুম, তখন বুঝতে পারলুম, ক্রোয়াসী রুটি কি রকম উপাদেয়, একটি মামুলী অমলেট বানাতে ফরাসি কতই না কেরদানি-কেরামতি দেখাতে পারে, পাকা টমাটো, কাঁচা শসা আর সামান্য লেটিসের পাতাকে একটুখানি মালমশলা লাগিয়ে কী অপুর্বস্যালড় নির্মাণ করতে পারে। মাস্টার্ড, উস্টারসস আর বিস্তর গোলমরিচ না মাখিয়েও যে ইয়োরোপীয় রান্না গলাধঃকরণ করা যায়। সেইটি হৃদয়ঙ্গম হল ফরাসি রান্না খেয়ে।
তাই আমার আনন্দ যে, ধীরে ধীরে একদিন ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত এদেশে বসেই হবে।
সোর্কল ফ্রাঁসে দিল্লিবাসীকে তার জন্য তৈরি করে আনছেন।
***
প্ৰবন্ধ পাঠের পর মসিয়ো মার্তে কয়েকটি রসালো গল্প বলেন। তিনি যে অনবদ্য ভাষায় এবং তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সঞ্চালনে গল্পগুলো পেশ করেছিলেন সে জিনিস তো আর কলি-কলমে ওতরাবে না-তাই গল্পটি পছন্দ না হলে মসিয়োর নিন্দা না করে দোষটা আমারই ঘাড়ে চাপাবেন।
এক রমণী গিয়েছেন এক সাকিয়াট্রিস্টের কাছে। তিনি ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার তাঁকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। অত কষ্টে সুযোগ পাওয়ার পর রমণী বললেন, ‘ডাক্তার, আমাকে অতশত বোঝাচ্ছেন কেন? আমি এসেছি আমার স্বামীর চিকিৎসা করাতে।’
ডাক্তার বললেন, ‘ও! তার কি হয়েছে?’
রমণী বললেন, ‘ঠিক ঠিক বলতে পারব না। তবে এইটুকু জানি, তাঁর বিশ্বাস তিনি সীল মাছ।’
‘বলেন কি? তা তিনি এখন কোথায়?’
তিনি বারান্দায় বসে আছেন।’
‘তাঁকে নিয়ে আসুন তো, দেখি, ব্যাপারটা কি।’
ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সীল মাছ।
ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন
দেশে বিদেশে বহুবার দেখিয়াছি যে, ইংরাজ ও ফরাসির প্রশ্নে ভারতীয় সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ (১) ভারতীয়রা স্বীয় ঐতিহ্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন-ইহার জন্য প্রধান আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী। (২) বিদেশী রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা-সে। জ্ঞান থাকিলে ভারতীয় তৎক্ষণাৎ বিদেশীকে চক্ষে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে তাহা অন্যরূপে বা অল্প কিয়দিন পূর্বে বিদেশীরাও করিত। নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে ও আশা করি কোনো কোনো ভারতীয়ের উপকারও হইবে।
বিদেশী : তোমাকে সেদিন ফির্পোতে দাওয়াত করিয়াছিলাম। তুমি টালবাহানা দিয়া পলাইলে। শুনিলাম, শেষটায় নাকি আমজাদীয়া হোটেলে খাইতে গিয়াছিলে। ফির্পোর খানা রাধে ত্ৰিভুবন-বিখ্যাত ফরাসিস শেফ দ্য কুইজিন। সেই শেফকে উপেক্ষা করিয়া তুমি কোন জঙ্গলীর রান্না খাইতে গেলে!
ভারতীয় : তোমাদের রান্নার অন্য গুণাগুণ বিচারের পূর্বে একটি অত্যন্ত সাধারণ বস্তুর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লক্ষ্য করিয়াছ কি না জানি না যে, তোমাদের রান্নায় তিক্ত টক ও ঝাল এই তিন রসের অভাব। অর্থাৎ ছয় রসের অর্ধেক নাই—ঝাল কিছু কিছু দাও বটে কিন্তু তাও বোতলে পুরিয়া টেবিলে রাখ, কারণ ঐ রাসটির প্রতি তোমাদের সন্দেহ ও ভয় এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। কাজেই তোমাদের খানা খাইয়াই বলা যায় যে, আর যে গুণই থাকুক, বৈচিত্ৰ্য তোমাদের রান্নায় থাকিবে না। শুধু লবণ আর মিষ্ট এই সা, রে লইয়া তোমরা আর কি সুর ভাঁজিবে? দুই-তারা লইয়া বীণার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও? আমজাদীয়ার ‘জঙ্গলী’ও তাই তোমার শেফকে অনায়াসে হারাইয়া দিবে। দ্বিতীয়ত, তোমাদের ডাইনিং টেবিলে ও রান্নাঘরে কোনো তফাত নাই। তোমরা ক্রুয়েট নামক ভাঙাবোতল-শিশিওয়ালার একটা ঝুড়ি টেবিলের উপর রাখ। নিতান্ত রসকষহীন সিদ্ধ অথবা অগ্নিপক্ক বস্তু যদি কেহ গলাধঃকরণ না করিতে পারে তবে তাহাতে ডাইনিং টেবিলে পাকা রাঁধুনী সাজিতে হয়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ সংযোগ করিতে গিয়ে অলিভ ওয়েল ঢাল, উগ্রতা উৎপাদনের জন্য রাই সরিষার (মাস্টার্ড) প্রলেপ দাও, কটু করিবার জন্য গোলমরিচের গুড়া ছিটাও,–বোতলটার আবার ছিদ্র রুদ্ধ বলিয়া তাহাকে লইয়া ধস্তাধস্তি করিয়ে স্কন্ধদেশস্থ অস্থিচ্যূতি ও ধৈৰ্য্যচ্যূতি যুগপৎ অতি অবশ্য ঘটে,-ভীতু পাচক বড় সাহেবের ভয়ে লবণও দিয়াছে কম-লক্ষ্য করিয়াছি কি শতকরা আশিজন সুপ মুখে দিবার পূর্বেই নুন ছিটাইয়া লয়?-অতএব লবণ ঢালো। তৎসত্ত্বেও যখন দেখিলে যে ভোজদ্রব্য পূর্ববৎ বিস্বাদই রহিয়া গিয়াছে তখন তাহাতে সস নামক কিন্তুতকিমাকার তরল দ্রব্য সিঞ্চন করো। তোমার গাত্র যদি পাচক রক্ত থাকে অবশ্য তুমি তাবৎ প্রলেপশিঞ্চন অনুপান-সম্মত বা মেকদার-মাফিখ করিতে পারো, কিন্তু আমি বাপু ‘ভদ্রলোকে’র ছেলে, বাড়িতে মা-মাসিরা ঐ কর্মটি রান্নাঘরে রন্ধন করিবার সময় করিয়া থাকেন। খানার ঘর আর রান্নাঘরে কি তফাৎ নেই?
সায়েব : রুচিভেদ আছে বলিয়াই তো এত বায়নাক্কা।
ভারতীয় : ঐ সব জ্যেষ্ঠতাতত্ত্ব আমার সঙ্গে করিও না। তাই যদি হইবে তবে খানাঘরেই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া মাংস সিদ্ধ করো না কেন, গ্রিল কাবাব ঝলসাও না কেন? কেহ অর্ধপক্ক মাংস পছন্দ করে, কেহ পূৰ্ণপক্ক। সেখানেও তো রুচিভেদ; তবে পাচকের হাতে ঐ কর্মটি ছাড়িয়া দাও কেন? আসল কথা, এই রুচিভেদ স্বীকার করিয়াও পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্যপন্থা বাহির করিয়া লাহে ও গুণীরা সেইটি স্বীকার করিয়া অমৃতলোকে পৌঁছেন। রুচিভেদ থাকা সত্ত্বেও গুণীরা সেক্সপীয়র কালিদাস পছন্দ করেন। কবি কখনো যমক, অনুপ্রাস, উপমা আখ্যানবস্তুর পৃথক পৃথক নির্ঘন্ট পৃথক পৃথক পুস্তকে দিয়া বলেন না রুচিমাফিক মেকদার-অন পানযোগে কাব্যসৃষ্টি করিয়া রসাস্বাদন করো।
সায়েব : সে কথা থাকুক। কিন্তু আমজাদীয়ার খানা খাইলে তো হাত দিয়া; সেখানে তো ছুরি-কাঁটার বন্দোবস্ত নাই।
ভারতীয় : না, আছে। ভারতবর্ষ তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া দিন দিন এমনি অসভ্য হইয়া পড়িতেছে যে, ভারতীয়রাও ছুরি-কাঁটা ধরিতে শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। এ নোংরামি করিবার কি প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।
সায়েব : নোংরামি? সে কি কথা?
ভারতীয় : নিশ্চয়ই। ঐ তো রহিয়াছে তোমার ছুরি, কাঁটা, চামচ; ঐ তো ন্যাপকিনা। ঘষো আর দেখো, কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যেটুকু বাহির হইবে না, তাহা খাদ্যরস সংযোগে অগোচরে পেটে যাইবে। আর আমি আমার আঙুল ঘষি দেখো কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যদি আমার আঙুল ময়লা হয়ই, তবে আমি এখনই টয়লেট ঘরে গিয়ে আচ্ছা! করিয়া হাত ধুইয়া লইব। তুমি যদি ছুরি-কাঁটা লইয়া ঐদিকে ধাওয়া করো। তবে ম্যানেজার পুলিশ ডাকিবে, ভাবিবে চৌর্যবৃত্তিতে তোমার হাতেখড়ি হইয়াছে মাত্র। আর শেষ কথাটিও শুনিয়া লও, আমারি আঙুল আমি আমারি মুখে দিতেছি; তুমি যে কাঁটা-চামচ মুখে দিতেছ। সেগুলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্তের অধরোষ্ঠে এবং আস্যগহ্বরেও নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে তাহার সন্দেশ রাখো কি? চীনারা তোমাদের তুলনায় পরিষ্কার। খাইবার কাঠি সঙ্গে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করে!
সায়েব : সে কথা থাকুক (ধুয়া)।
ভারতীয় : হ্যাঁ, আলোচনাটাই আমার পক্ষেও মর্মঘাতী। আমারি এক বাঙালি খ্রিস্টান বন্ধু কাঁটা দিয়া ইলিশ মাছ খাইতে যান—বেজায় সায়েব কিনা-ফলে ইলিশাস্থি তাহার গলাস্থ হয় এমনি বেকায়দা বেদুরস্তভাবে যে, তাহার শরীরের অস্থিগুলি এখন গোরস্তানে চিরতের বস্তি গাড়িয়াছে (অশ্রু বর্ষণ)।
সায়েব : আহা! তবে ইলিশ না খাইলেই হয়।
ভারতীয় : ইংরাজ হইয়া বেকান-আন্ডা না খাইলেই হয়; ফরাসি হইয়া শ্যাম্পেন না। খাইলেই হয়; জর্মন হইয়া সসিজ না খাইলেই হয়; বাঙালি হইয়া ইলিশ না খাইলেই হয়, অনশনে প্ৰাণত্যাগ করিলেও হয়; আত্মহত্যা করিলেও হয়। লাজ করে না বলিতে? বাংলার বুকের উপর বসিয়া হোম হইতে টিনস্থ বেকন না পাইলে ব্রিটিশ ট্রেডিশন ইন ডেঞ্জার বলিয়া কমিশন বসাইতে চাহো, আর আমি গঙ্গার পারে বসিয়া গঙ্গার ইলিশ খাইব না? তাজ্জব কথা!
সায়েব : সে কথা থাকুক (ধুয়া)। কিন্তু ঐ বলিলে তোমাদের মেয়েরা রান্না করেন, র্তাহারা কি শুধুই রান্না করেন? তাহারা এই নির্মম পর্দা প্ৰথা মানেন কেন?
ভারতীয় : সে তাহারা মানেন; তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।
সায়েব : তাহাদিগের সঙ্গে তো দেখাই হয় না।
ভারতীয় : সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।
সায়েব : (চিন্তিত মনে) কথাটা কি একটু কড়া হইল না? আমরা কি এতই খারাপ?
ভারতীয় : খারাপ ভালোর কথা জানিনা সাহেব। তবে ১৭৫৭ সালে তোমাদের সাথে পীরিতিসায়রে সিনান করিতে গিয়া শুধু যে আমাদের সকলি গরল ভেল। তাহা নয়, স্বরাজগামছাখানা হারাইয়া ফেলিয়া দুইশত শীত বৎসর ধরিয়া আকণ্ঠ দৈন্য-দুৰ্দশ-পঙ্কে নিমগ্ন-ডাঙ্গায় উঠিবার উপায় নাই। পুরুষদের তো এই অবস্থা। তাই মেয়েরা অন্তরমহলে তোমাদিগকে quit করিয়া বসিয়া আছেন।
সায়েব : এ সব তো বাইরের কথা; তোমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য—
ভারতীয় : আরেকদিন হইবে। উপস্থিত আমাকে Quit India গাহিতে রাস্তায় যাইতে হইবে।
(ডিসেম্বর ১৯৪৫)
ইন্দ্ৰলুপ্ত
(আবু সাঈদ আইয়ুবকে)
ঘরের দাওয়ায়, তেঁতুলের ছাওয়ায়, মাঠের হাওয়ায়
খাওয়া-দাওয়ায়
শান্তি নেই, গরমেরও ক্লান্তি নেই।
সবুজ ঘাস হল হলদে, তারপর ফিকে।
দস্যি কাল-বোশেখী বাঁশের বনে ত্রিবিক্রমে বিক্রমে
তাদের কোমর ভেঙে নামল মাঠে।
লাথি মেরে বেঁটিয়ে নিয়ে গেল তার শুকনো শেকড়
বেরিয়ে পড়ল শুভ্ৰ, উন্ম, নগ্ন মৃত্তিকা।
মাঠের টাক–
আমার টাকের মতো।
কলনের ঘন বনে
নিদাঘের তপ্ত কাফে কোণে
তুমি বসে আনমনে
—আমার চুলের ঘুঙুর তোমার নাচাল নয়ন নীল
কালোকে নীলোতে নাৎসি হারাতে পেল কি গোপন মিল?–
রাইনের ওয়াইনের মৃদু গন্ধ,
একচোখা রেডিয়োটা করে কটমট
ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘ফ্রল্যান, Gruless Gott!
বেতারের সুরাটা টাঙ্গো না ফক্স-স্ট্রট?’
চট করে চটে যাও পাছে!
তুমি রূপসিনী বন্দিনী
নরদেশী নন্দিনী।
তোমার প্রেম এল যে
শ্রাবণের বর্ষণের ধারা নিয়ে
চারদিকে টেনে দিয়ে
ঘনকৃষ্ণ সজল যামিনী যাননিকা।
সে বিরাট বিলুপ্তির বিস্মরণে
শুধু আমার চেতনার ছয় ঋতু
আর তোমার চেতনার চার ঋতুর বিজড়িত নিবিড় স্পৰ্শ–
লাল ঠোঁট দিয়া বঁধূয়া আমার
পড়িল মন্ত্র কাল
দেহলি রুধিয়া হিয়ারে বান্ধিল
পাতিয়া দেহের জাল।
মুখে মুখ দিয়া হিয়ায় হিয়ায়
পরশে পরশে রাখি
বাহু বাহুপাশে ঘন ঘন শ্বাসে
দেহে দেহ দিল ঢাকি।
হঠাৎ দামিনী ধমকালো
বিদ্যুৎ চমকালো
দেখি, নীল চোখ
কাতরে শুধাই একি
তোমার নয়নে দেখি,
তোমার দেশের নীলাভ আকাশ
মায়া রচিছে কি?
তোমার বক্ষতলে
আমার দেশের শ্বেতপদ্ম কি
ফুটিল লক্ষ দলে?
রাত পোহালি। বর্ষণ থেমেছে।
কিন্তু কোথায় শরতের শান্তি, হেমন্তের পূর্ণতা?
ঋতুচক্ৰ গেল উলটে–
যমুনার জলও একদিন উজান বয়েছিল।–
কোন ঝড় তোমাকে নিয়ে গেল ছিনিয়ে
কোন ঝড় আমাকে নিয়ে গেল ঝেঁটিয়ে?
বেরিয়ে এল মাঠের টাক,
আমার টাকা।
আমার জীবনে ইন্দু লুপ্ত
আমার কপালে ইন্দ্রলুপ্ত।।
উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়–নির্বাসিতের আত্মকথা
কোনো কোনো বই পড়ে লেখকেরা আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় নিরাশ হন। যাদের সত্যকার শক্তি আছে, তাদের কথা হচ্ছে না, আমি ভাবছি আমার আর আমার মত আর পাঁচজন কমজোর লেখকের কথা।
প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পুনরায় ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’ পুস্তিকাখনি আদ্যন্ত পড়লুম। পাঠকমাত্রই জানেন, ছেলেবেলার পড়া বই পরিণত বয়সে পড়ে মানুষ সাধারণত হতাশ হয়। নির্বাসিতের’ বেলা আমার হল বিপরীত অনুভূতি, বুঝতে পারলুম, কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত মধুর বাক্যভঙ্গি, কত উজ্জ্বল রসবোক্য, কত করুণ ঘটনার ব্যঞ্জনা তখন চোখে পড়ে। সাধুভাষার মাধ্যমে যে এত ঝকঝকে বর্ণনা করা যায়, সে ভাষাকে যে এতখানি চটুল গতি দিতে পারা যায়, ‘নির্বাসিত’ যারা পড়েন নি, তারা কল্পনামাত্র করতে পারবেন না।
কিন্তু প্রশ্ন, এই বই পড়ে আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হলুম কেন?
হয়, এ রকম একখানা মণির খনির মত বইয়ের চারিটি সংস্করণ হল ত্ৰিশ বৎসরে! তাহলে আর আমাদের ভরসা রইল কোথায়?
***
১৯২১ (দু-চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে) ইংরেজিতে একদিন শান্তিনিকেতনে লাইব্রেরিতে দেখি একগাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরিতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রতি মেলে বহু ভাষায় বিস্তর পুস্তক পেতেন। তার পড়া হয়ে গেলে তার অধিকাংশ বিশ্বভারতীর পুস্তকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি, ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’।
বয়স অল্প ছিল, তাই উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জানা ছিল না। বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিঃশ্বাসে শেষ করলুম। কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছি নে, এ বই সত্যসত্যই আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে। ‘পৃথিবীর সব ভাষাতেই এরকম বই বিরল; বাঙলাতে তো বটেই।’
পরদিন সকালবেলা শুরুদেবের ক্লাসে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’ কেউ পড়েছি?’ বইখানা প্ৰকাশিত হওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে; তিনি সেখানা পড়ে লাইব্রেরিতে পাঠান, সেখান থেকে আমি সেটাকে কত্তজা করে এনেছি, অন্যেরা পড়বার সুযোগ পাবেন কি করে? বয়স তখন অল্প, ভারি গর্ব অনুভব করলুম।
বললুম, ‘পড়েছি।’
শুধালেন, ‘কি রকম লাগল?’
আমি বললুম, ‘খুব ভালো বই।’
রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘আশ্চর্য বই হয়েছে! এ রকম বই বাঙলাতে কম পড়েছি।’
বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর হুবহু মনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি প্রকারে তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার খাতাতে টোকা ছিল এবং সে খাত কাবুল-বিদ্রোহের সময় লোপ পায়। তবে একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে যে, রবীন্দ্ৰনাথ বইখানার অতি উচ্ছসিত প্ৰশংসা করেছিলেন।
বিখ্যাত লেখককে দেখার সাধ সকলেরই হয়। আমি যে সে কারণে উপেন্দ্ৰনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম তা নয়। আমার ইচ্ছা ছিল দেখবার যে বারো বৎসর নরকযন্ত্রণার পর তিনি যে তার নিদারুণ অভিজ্ঞতাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে প্ৰকাশ করলেন তার কতখানি সত্যই তার চরিত্রবলের দরুন। এই বিশেষ রূপ নিল আর কতখানি নিছক সাহিত্যশৈলী মাত্র। অর্থাৎ তিনি কি সত্যই এখনো সুরসিক ব্যক্তি, না অদৃষ্টের নিপীড়নে তিক্তস্বভাব হয়ে গিয়েছেন।
গিয়ে দেখি পিতা-পুত্র বসে আছেন।
বেশ নাদুস-নুদুসু চেহারা (পরবর্তী যুগে তিনি রোগ হয়ে গিয়েছিলেন), হাসিভরা মুখ আর আমার মত একটা আড়াই ফোটা ছোকরাকে যে আদর করে কাছে বসালেন, তার থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম যে, তাঁর ভিতরে মানুষকে কাছে টেনে আনবার কোন আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল, যার জন্যে বাঙলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় তার চতুর্দিকে জড় হয়েছিল।
ছেলেটিকেও বড় ভালো লাগলো। বড্ড লাজুক আর যে সামান্য দু’একটি কথা বলল, তার থেকে বুঝলুম, বাপকে সে শুধু যে ভক্তি-শ্রদ্ধাই করে তা নয়, গভীরভাবে ভালোও বাসে।
অটোগ্রাফ-শিকারের ব্যসন তখন বাঙলা দেশে চালু হয় নি। তবে সামান্য যে দু’একজন তখনকার দিনে এ ব্যসনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু স্বাক্ষরেই সন্তুষ্ট হতেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কুটেশন বা আপন বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন। আমার অটোগ্রাফে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্ৰ, অবনীন্দ্রনাথ, প্ৰফুল্ল রায়, লেভি, অ্যাভুজ ইত্যাদির লেখা তো ছিলই, তার উপর গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, কারপেলেজের ছবিও ছিল।
উপেনবাবুকে বইখানা এগিয়ে দিলুম।
এর পিছনে আবার একটুখানি ইতিহাস আছে।
বাজে-শিবপুরে শরৎচন্দ্ৰকে যখন তাঁর স্বাক্ষর এবং কিছু একটা লেখার জন্য চেপে ধরেছিলুম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বিশেষ করে তার কাছেই এলুম কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম, ‘আপনার লেখা পড়ে আপনার কাছে না। আসাটাই তো আশ্চর্য!’ শরৎবাবু একটুখানি ভেবে লিখে দিলেন, ‘দেশের কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।’
আমি জানি শরৎচন্দ্ৰ কেন ঐ কথাটি লিখেছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেস নিয়ে মেতেছিলেন।
তারপর সেই বই যখন রবীন্দ্রনাথকে দিলুম, তখন তিনি শরৎচন্দ্রের বচন পড়ে লিখে দিলেন,–
‘আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে যে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।’
এর ইতিহাস বাঙালিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রী নিয়ে তখন রবীন্দ্ৰ-শরৎচন্দ্রের তর্ক আলোচনা হচ্ছিল।
উপেনবাবুকে অটোগ্রাফ দিতে তিনি দুটি লেখা পড়ে লিখে দিলেন,—
‘সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।’
***
ছেলেবালায় বইখানা পড়েছিলুম এক নিশ্বাসে কিন্তু আবার যখন সেদিন বইখানা কিনে এনে পড়তে গেলুম তখন বহুবার বইখানা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতে হল। বয়স হয়েছে, এখন অল্পতেই চোখে জল আসে আর এ বই-য়েতে বেদনার কাহিনী অল্পের উপর দিয়ে শেষ হয় নি। সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব বোধ হয়। বইখানির সেখানেই। উপেন্দ্রনাথ যদি দস্তয়েফস্কির মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তাঁর কারাবাস আর আন্দামান-জীবন (জীবন না বলে ‘মৃত্যু’ বলাই ঠিক) বর্ণনা করতেন। তবে আমাদের মনে কোন জাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হত বলা সুকঠিন। কিন্তু এই যে তিনি নির্বাসিতদের নিদারুণ দুঃখ-দুৰ্দৈবের বহুতর কাহিনী প্রতিবারেই সংক্ষিপ্ততম বর্ণনায় শেষ করে দিয়েছেন। এতে করেই আমাদের হৃদয়কে মথিত করেছে কত বেশি। সেটা হল প্রকৃত শক্তিশালী লেখকের লক্ষণ। যেটুকুর ব্যঞ্জনার পাখা প্রয়োজন উপেন্দ্রনাথ সেইটুকু মাত্র দিয়েই আমাদের উড়িয়ে দিলেন। উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং যে উদ্ধৃতি আপন পুস্তকে ব্যবহার করেছেন। আমি সেইটে দিয়ে তার এ অলৌকিক ক্ষমতার প্রশস্তি গাই;
‘ধন্য ধন্য পিতা দশমেস গুরু
যিন চিড়িয়াঁসে বাজ তোড়ায়ে’
‘ধন্য ধন্য পিতঃ, হে দশম গুরু! চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলোঁ; তুমি ধন্য।’(১)
উপেন্দ্রনাথ দস্তয়েফ্স্কির মতো শক্তিশালী লেখক নন; দস্তয়েফ্স্কির মতো বহুমুখী প্রতিভা তীব্র ছিল না। কিন্তু এ-কথা বার বার বলব দস্তয়েফ্স্কির সাইবেরিয়া কারাবাস উপেন্দ্রনাথের আত্মকথার কাছে অতি নিশ্চয় হার মানে।
অনেক লোকেরই আছে কিন্তু একই ভাষার ভিতর এত রকমের ভাষা লিখতে পারে কজন? এক শ সত্তর পাতার বইয়ে ফলাও করে বর্ণনা দেবার স্থান নেই। অথচ তার মাঝখানেই দেখুন, সামান্য কয়টি ছত্রে কী অপরূপ গুরুগম্ভীর বর্ণনা;–
‘গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পশী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদে কাঁপয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ববন্ধনমুক্ত–দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখনও স্পর্শ করিতে পরিবে না।’(২)
পড়ে মনে হয় যেন বিবেকানন্দের কালীরূপ বর্ণনা শুনছি,–
‘নিঃশেষে নিবেছে তারাদল
মেঘ আসি আবরিছে মেঘ
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার
গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত পরান
বহির্গত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমুলে উপাড়ি
ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে’।(৩)
উপরের গম্ভীর গদ্য পড়ার পর যখন দেখি অত্যন্ত দিশী ভাষায়ও তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। ঠিক তেমনি জোর দিয়ে তখন আর বিস্ময়ের অস্ত থাকে না। শুধু যে সংস্কৃত শব্দের ওজস এবং প্রসার সম্বন্ধে তিনি সচেতন তাই নয়, কলকাতা অঞ্চলের পুরোপাক্কাতে তো কড়া ভাষাতেও তার তেমনি কায়েমি দখল।
‘বারীন বলিল-’এতদিন স্যাঙ্গাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে তারা সবাই প্ৰস্তুত; শুধু বাঙলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না, সব ঢুঁঢ়ু। কোথাও কিছু নেই; শুধু কর্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। খুব কষে ব্যাটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি’।(৪)
এ-ভাষা হুতোমের ভাষা; এর ব্যবহার অতি অল্প লেখকেই করেছেন।
এককালে পশ্চিম-বাঙলার লোকও আরবী-ফার্সী শব্দে প্রসাদগুণ জানতেন ও কায়দামাফিক সেগুলো ব্যবহার করে ভাষার জৌলুস বাড়াতে কসুর করতেন না। ক্রমে ক্রমে এ ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গে লোপ পায় অথচ পূর্ববাঙলার লেখকদের মেকদারবোধ কম ছিল বলে তারা এ বাবাদে অনেক জায়গায় লাভের বদলে লোকসানই করেছেন বেশি। উপেন্দ্রনাথ তাগমাফিক আরবী-ফার্সীও ‘এস্তেমাল’ করতে জানতেন।
‘কোনরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারীর খানা খাওয়াইয়া তাহার গোঁফ ছাটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহস্তে যে খোদাতাল্লা তাহদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন, এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে।’(৫)
কিন্তু উপেন্দ্ৰনাথ ছিলেন একদম ন-সিকে বাঙালি। তাই, ‘আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলকার হাত হইতে নির্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদগতির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই-আমরা বাঙালি।’(৬)
বাঙালির এরকম নেতিবাচক রমণীয় সংজ্ঞা আমি আর কোথাও শুনি নি। কিন্তু, এসব তাবৎ বস্তু বাহ্য।
না সংস্কৃত, না। আরবী-ফারসি, না। কলকত্তাই সব কিছু ছাড়িয়ে তিনি যে খাঁটি মেটে বাঙলা লিখতে পারতেন তার কাছে দাঁড়াতে পারেন আজকের দিনের ক’জন লেখক?
‘শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কিরকম খাদ্য খাইতে হয়। জিজ্ঞেস করায় শচীন লপসীর নাম করিল। পাছে লপসীর স্বরূপ প্ৰকাশ পাইয়া পিতার মনে কষ্ট হয়। সেই ভয়ে শচীন লপসীর গুণগ্ৰাণ বৰ্ণনা করিতে করিতে বলিল, ‘লপসী খুব পুষ্টিকর জিনিস।’ পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন-’বাড়িতে ছেলে আমার পোলাও-এর বাটি টান মেরে ফেলে দিত; আর আজ লিপসী তার কাছে পুষ্টিকর জিনিস।’ ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয় তাহা কখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই, তবে তাহার ক্ষীণ আভাস যে একেবারে পাই নাই তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমরা সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়তো এ জন্মে। তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলো আমরা সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল।‘(৭)
***
স্থাপত্যের বেলা ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায়, কিন্তু সাহিত্যে অতটা সোজা নয়। তাজমহলকে পাঁচগুণ বড় করে দিলে তার লালিত্য সম্পূর্ণ লোপ পেত, যদিও ঐ বিরাট বস্তু তখন আমাদের মনকে বিস্ময়বিমূঢ় করে দিত, আর আমরা স্তম্ভিত হয়ে বলতুম, ‘এ কী এলাহী ব্যাপার!’ ফলে শাহজাহান যে প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ইমারতখানা তৈরি করেছিলেন, সেকথা বেবাক ভুলে যৌতুম।
আর তাজমহলকে ছোট করে দিলে কি হয়, তা তো নিত্যি নিত্যি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শ্বেতপাথরের ক্ষুদে তাজমহল মেলা লোক ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখেন। পাঁচজন তার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি আগ্ৰায় গিয়েছিলেন কবে? ভদ্রলোকের আগ্ৰা গমন সফল হল-ক্ষুদে তাজ যে কোণে সেই কোণেই পড়ে রইল।
সাহিত্যের বেলাও অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, ‘এ উপন্যাসখানা যেন বড্ড ফেনিয়ে লেখা হয়েছে কিংবা অন্য আরেকখানা এতটা উধৰ্বশ্বাসে না লিখে আরো ধীরে-মস্থরে লিখলে ঠিক আয়তনে গিয়ে দাঁড়াত।’ ‘যোগাযোগ’ পড়ে মনে হয় না, এই বইখানাকে বড় কিংবা ছোট করা যেত না, ‘গোরা’র বেলা মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, হয়তো এ অনবদ্য পুস্তকখানা আরো ছোট করলে তার মূল্য বাড়ত।
আমার মনে হয় ‘আত্মকথা’ সংক্ষেপে লেখা বলে সেটি আমাদের মনে যে গভীর * ছাপ রেখে গিয়েছে, দীর্ঘতর হলে হয়তো সেরকম অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত না। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বইখানা লিরিক না করে এপিক করলেই ভালো হত। এ বই যদি ‘ওয়ার অ্যান্ড পীসের মত বিরাট ক্যানভাস নিয়ে চিত্রিত করা হত। তবে বুঝি তার উপযোগী মূল্য দেওয়া হত। কিন্তু এ বিষয়ে কারো মনে দ্বিধা উপস্থিত হবে না যে, লিরিক হিসাবে এ বই এর চেয়ে কি বড়, কি ছোট কিছুই করা যেত না।
বই আরম্ভ করতেই চোখে পড়ে প্রথম বিপ্লবী যুগের এই তরুণদের হৃদয় কি অদ্ভুত সাহস আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী অবিশ্বাস্য তাচ্ছিল্যে ভরা ছিল। পরবর্তী যুগে ইংরেজের জেলখানার স্বরূপ আমরা চিনেছিলুম এবং শেষের দিকে জেল-ভীতি সাধারণের মন থেকে তো এক রকম প্রায় উঠেই গিয়েছিল, কিন্তু যে যুগে এঁরা হাসিমুখে কারাবরণ করেছিলেন, সে যুগের যুবকদের মেরুদণ্ড কতখানি দৃঢ় ছিল, আজ তো আমরা তার কল্পনাই করতে পারিনে। উল্লাস, কানাই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে হেসেছিল—যেন কঁধ থেকে বেঁচে থাকার একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। আজ যখন বাঙলাদেশের দিকে তাকাই, তখন বারংবার শিরে করাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করে, ‘হে ভগবান, সে যুগে তুমি অকৃপণ হস্তে বাঙলা দেশকে এত দিয়েছিলে বলেই কি আজ তোমার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে?’
অথচ রুদ্র মহাকাল এই তরুণদের হৃদয়ে এবং জীবনে যে তাণ্ডব নৃত্য করে গেলেন, যার প্রতি পদক্ষেপে বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কুটির আন্দোলিত হল, বাঙালি হিন্দুর ইষ্টদেবী কালী করালী যখন বারংবার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ‘মৈ ভূখা হাঁ তখন যে এই বঙ্গসন্তানগণ প্রতিবারে গম্ভীরতর হুঙ্কার দিয়ে বলল,-
‘কালী তুই করালরূপিণী/আয় মাগো আয় মোর কাছে।’
যুপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় স্কন্ধ দিয়ে বলল, হানো, তোমার খড়গ হানো, তখনকার সেই বিচিত্র ছবি উপেন্দ্ৰনাথ কী দম্ভহীন অনাড়ম্বর অনাসক্তিতে চিত্রিত করে গেলেন।
দক্ষিণ ভারতের মথুরা, মাদুরায় এক তামিল ব্রাহ্মাণের বাড়িতে কয়েক মাস বাস করার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। গৃহকর্ত্রী প্রতি প্ৰত্যুষে প্রহরাধিককাল পূর্বমুখী হয়ে রুদ্র-বীণা বাজাতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, ‘আজ আপনি কি বাজালেন বলুন তো। আমার মনের সব দুশ্চিন্তা যেন লোপ পেলা’ বললেন, ‘এর নাম ‘শঙ্করবরণম’–সন্ন্যাসী রাগীও একে বলা হয়। কারণ এ রাগে আদি, বীর, করুণ কোনো প্রকারের রস নেই বলে একে শান্তরসও বলা হয়। কিন্তু শান্ত অবস্থাকে তো রিসাবস্থা বলা চলে না, তাই এর নাম সন্ন্যাস রাগ।’
উপেন্দ্রনাথের মূল রাগ সন্ন্যাস রাগ।
অথচ এই পুস্তিকা হাস্যরসে সমুজ্জ্বল।
তাহলে তো পরস্পরবিরোধী কথা বলা হল। কিন্তু তা নয়। উপেন্দ্ৰনাথ তার সহকর্মীদের জীবন তথা বাঙলাদেশের পতনঅভু্যদায়বন্ধুরপন্থা নিরীক্ষণ করছেন অনান্তীয় বৈরাগ্যে—তাই তার মূল রাগ সন্ন্যাস—এবং তার প্রকাশ দিয়েছেন হাস্যরসের মাধ্যমে, দুঃখ-দুৰ্দৈবকে নিদারুণ তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ দিয়ে এ বড় কঠিন কর্ম-কঠোর সাধনা এবং বিধিদত্ত সাহিত্যরস একাধারে না থাকলে এ ভানুমতী অসম্ভব।
আমার প্রিয় চরিত্র জন কুইক সন্ট্র। উপেন্দ্রনাথ বিপরীত ডন।
ডন এবং উপেন্দ্রনাথের সাহস অসীম; দুইজনেই পরের বিপদে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শাণিত তরবারি নিয়ে আক্রমণ করেন, অন্যায় অত্যাচারের সামনে দুজনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোহিতরঙে রঞ্জিত দেখেন।
পার্থক্য শুধু এইটুকু, উইন্ডমিলকে ডন মনে করেন দৈত্য, দাসীকে মনে করেন রাজনন্দিনী, ভেড়ার পালকে মনে করেন জাদুঘরের মন্ত্রসম্মোহিত পরীর দল।
আর উপেন্দ্ৰনাথ দেখেন বিপরীত। কারাগারকে ভাবেন রঙ্গালয়, কারারক্ষককে মনে করেন। সার্কাসের সং, পুলিশ বাহিনীকে মনে করেন ভেড়ার পাল।
এই নব ডন কুইক্সট্কে বার বার নমস্কার।।
——
(১) নির্বাসিতের আত্মকথা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৯৬০।
(২) আত্মকথা, পৃঃ ৬৬।
(৩) সত্যেন দত্তের অনুবাদ।
(৪) আত্মকথা, পৃঃ ৩৩।
(৫) পৃঃ ১১৯।
(৬) পৃঃ ১২১।
(৭) পৃঃ ৬৯, ৭০।
ঋতালী
ইসমাইলি খোজা সম্প্রদায়ের গুরুপুত্র প্রিন্স আলী খানের সঙ্গে শ্ৰীমতী ঋতা (স্পেনিশ ভাষায় যখন t অক্ষরের উচ্চারণ বাংলা ‘ত’য়ের মত হয় তখন r টাকে ‘ঋ’ বানাতে কারো বড় বেশি আপত্তি করা উচিত নয়) হেওয়ার্থের শাদী হয়েছে আর বিয়ের দাওয়াতে নাকি হাজার দেড়েক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়া হয়েছে।
ফ্রান্সের যে অঞ্চলে শাদীটা হয়েছে সেখানে শ্যাম্পেন মাগগী নয়। তবু যে বেশ কিছু পয়সা খরচা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ জর্মনরা নাকি ফ্রান্স ত্যাগ করার পূর্বে প্রাণভরে শ্যাম্পেন খেয়ে ফ্রান্সের তাবৎ শ্যাম্পেনের গুদোম উজাড় করে দিয়ে যায়। বছর সাতেক না যাওয়া পর্যন্ত ১৯৪৫-এর শ্যাম্পেন খাওয়ার মত ‘পরিপক্ক’ হবে না।—কাজেই আলী খান নিশ্চয়ই ৪৫-এর আগেকার লুকোনো মাল গৌরীসেন পয়সা দিয়ে কিনেছেন। তা কিনুন, তার পয়সার অভাব নেই। কিন্তু প্রশ্ন, মুসলমান ধর্মে যখন মদ বারণ তখন ধর্মগুরুর বড় ব্যাটা (পরে ইনিই গুরু হবেন)। এ খবরটা ছাপতে দিলেন কোন সাহসে?
বোম্বায়ে যখন বাস করতুম তখন আলী খানের খোজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তখন কিছুদিন তাদের ইতিহাস, শাস্ত্ৰ, আচার ব্যবহার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলুম। সেগুলি সত্যিই বহু রহস্যে ভরা।
খোজাদের বিশ্বাস, আদমকে সৃষ্টি করার সময় আল্লা তাঁর জ্যোতির খানিকটা তাঁর শরীরে ঢেলে দেন। সে জ্যোতি আদম থেকে বাংশানুক্রমে মহাপুরুষ মেসেজ (মুসা), নোয়া (নূহ), ইব্রাহাম (ইব্রাহিম), সলমন (সুলেমান), ডেভিড (দায়ুদ) হয়ে হয়ে শেষটায় মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে পৌঁছোয়। তারই এক অংশ তখন বর্তে মহম্মদে, অন্য অংশ তার আবার সেই দ্বিখণ্ডিত জ্যোতি সংযুক্ত হয়। তারপর সেই জ্যোতি বংশানুক্ৰমে চলে এসেছে প্রিন্স আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে। তিনি মারা গেলে আলী খান সেই জ্যোতি পাবেন।
কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের খোজারা আরেকটা বিশ্বাস জুড়ে দিয়েছেন। সে মত অনুসারে খোজারা বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু নয়বার মৎস্য কূৰ্ম ইত্যাদি রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং দশমবারে কল্কিরূপে যে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে, সেও খাঁটি; কিন্তু হিন্দুরা জানে না যে কল্কি বহুদিন হল অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছেন আলীরূপে মক্কা শহরে। এবং শুধু তাই নয়, সেই কল্কি অবতারের জ্যোতি তার ছেলে হুসেনে বর্তে ক্ৰমে ক্ৰমে বংশপরম্পরায় নেমে এসে উপস্থিত বিরাজ করছে আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে। তাই হজরত আলী হলেন কল্কি অবতার এবং সেই কল্কির জ্যোতি আগা খানের শরীরে আছে বলে তিনিও কল্কি অবতার। তাই খোজা ধর্মগ্রন্থে আগা খানের সম্পূর্ণ নাম লেখা হয় ‘দশবাঁ নকলঙ্ক অবতার আগা সুলতান মুহম্মদ সাহ’।
কিন্তু প্রশ্ন, খোজারা এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ করল কি প্রকারে? অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দশম-একাদশ শতাব্দীতে ইরানের ইসমাইলি সম্প্রদায় আপন দল বাড়াবার জন্য চতুর্দিকে মিশনারি পাঠান। (আরো নানা সম্প্রদায় তখনকার দিনে ইরানের বন্দর আব্বাস থেকে জাহাজে করে সমুদ্রতীরবতী সিন্ধু প্রদেশ আর কঠিয়াওয়াড়ে এসে আপন আপন মতবাদ প্রচার করতেন)। এই মিশনারিদের উপর কড়া হুকুম ছিল, দল বাড়াবার জন্য কারো ধর্মমত যদি খানিকটা গ্ৰহণ করতে হয় তাতে কোনো আপত্তি নেই—মোদ্দা কথা হচ্ছে, সংখ্যাবৃদ্ধি যে করেই হোক করতে হবে।
এই মিশনারিদের একজন এসে কাজ আরম্ভ করেন। কাঠিয়াওয়াড় এবং কচ্ছের লোহানা রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁরা ছিলেন বৈষ্ণব-কিন্তু পাঞ্চরাত্ৰ মতবাদের। এরা ইসমাইলি মতবাদের দিকে কেন আকৃষ্ট হলেন তার খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা যে এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করার সময় বিষ্ণুর অবতারবাদটা সঙ্গে এনেছিলেন, সে কথাটা আজও খোজাদের জমাতখানা’তে (খোজারা অন্যান্য মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁদের আপনি মসজিদের নাম ‘জমাতখানা’ বা সম্মেলনালয়) প্রকাশ পায় তাদের উপাসনার সময়। সর্বপ্রথম বিষ্ণুর নয় অবতারের নাম স্মরণ করা হয় বসে বসে এবং দশম অবতার আলী এবং হিজ হাইনেস দি আগা খানের নাম আরম্ভ হতেই সবাই উঠে দাঁড়ান।
গোঁড়া খোজারা বিশ্বাস করেন, স্বৰ্গে ঈশ্বর নেই। তিনি শরীর ধারণ করে আছেন আগা খান রূপে।
চন্দ্র, সূর্য তাঁর আদেশে চলে, তিনিই ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে সর্বসৃষ্টি ধ্বংস করতে পারেন, নূতন বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডও সৃষ্টি করতে পারেন।
এরকম বিশ্বাস যে বিংশ শতাব্দী—বা অন্য যে কোনো শতাব্দীতে-কেউ করতে পারে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল, কিন্তু যখন স্বকৰ্ণে শুনলুম, তখন আর অবিশ্বাস করি কি প্রকারে?
ভারতবর্ষে সুন্নি সম্প্রদায় খোজাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু ইরাণের সুন্নিরা অনেক কিছু জানেন বলে খোজা এবং তাঁদের জনক সম্প্রদায় ইসমাইল মতবাদকে বিধর্মী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কোরানে যখন বিষ্ণু এবং নয় অবতারের উল্লেখ নেই, এবং যেহেতু কোরান অবতারদের বিরুদ্ধে আপনি বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে তখন সুন্নি মতবাদ যে খোজা সম্প্রদায়কে বিধর্মী বলবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? খোজারা অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামান না, কারণ খোজার যদিও কোরানকে ‘ভালো কেতাব’ রূপে স্বীকার করেন, তবু কর্মক্ষেত্রে তারা মানেন কচ্ছ এবং গুজরাতী ভাষায় লিখিত নিজস্ব ‘গিনান’ গ্রন্থাবলীকে। ‘গিনান’ শব্দ সংস্কৃত ‘জ্ঞান’ শব্দ থেকে বেরিয়েছে এবং এ সব গিনান লিখেছেন খোজা ধর্মগুরুরা।
খোজারা তিনবার নামাজ পড়েন, এবং রোজার মাসে মাত্র একদিন উপোস করেন। তাও বেলা বারোটা পর্যন্ত।
কিন্তু সব চেয়ে বড় তত্ত্বকথা, আগা খান এত টাকা পেলেন কোথায়? তাঁর ঠাকুর্দা তো ইরান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। গত শতকের মাঝামাঝি। এইখানেই খোজা ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব লুক্কায়িত।
প্রতি জামাতখানাতে একটা করে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক থাকে। প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় প্রত্যেক খোজা এই সিন্দুকে আপন মুনাফা (কোনো কোনো স্থলে আমদানির) থেকে অষ্টমাংস ফেলে দেয় এবং এই সব টাকা যায় আগা খানের তহবিলে। তা ছাড়া পালা-পরবে: দান বলতে যা কিছু বোঝায় সবই ফেলা হয় এই সিন্দুকে এবং বহু খোজা মরার আগে তার তাবৎ ধনসম্পত্তি গুরু। আগা খানের নামে উইল করে দিয়ে যায়। খোজা সম্প্রদায়ের কারবার ব্যবসা জগৎজোড়া-শ্যাঙ্গাই থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত। কাজেই আগা খানের মাসিক আয় কত তার হিসাব নাকি স্বয়ং আগা খান ছাড়া কেউ জানে না।
তা জেনে আমাদের দরকারও নেই। এবং আমি জানি, এত সব তত্ত্বকথা শোনার পরও পাঠক শুধাবেন, কিন্তু যে শ্যাম্পেন নিয়ে আরম্ভ করেছিলে তার তো কোনো হিল্লে হল না। মদ যখন বারণ তখন আলী খান শ্যাম্পেন খান কি প্রকারে? তবে কি শ্যাম্পেন মদ নয়?
বিলক্ষণ! শ্যাম্পেনে আছে শতকরা প্ৰায় পনেরো অংশ মাদকদ্রব্য বা এলকহল। এবং যেহেতু শ্যাম্পেন খুললেই সোডার মত বুজবুজ করে, তাই তাতে আছে ছোট ছোট বুদ্বুদ। সেগুলো পেটে গিয়ে খোঁচা দেয় বলে নেশা হয় চট করে এবং স্টীল ওয়াইন বা শান্ত মদের তুলনায় অনেক বেশি। তবে?
খোজারা বলেন, ‘আলী খান একদিন স্বয়ং কল্কি অবতারের জ্যোতি পাবেন বলে তিনি এখন থেকেই পূতপবিত্র। কোনো বস্তু তাঁকে অপবিত্র করতে পারে না। তাই অপবিত্র মদ তার হস্তস্পর্শ লাভ করা মাত্রই পবিত্র হয়ে যায়।’
এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম, সেগুলো দলিল দস্তাবেজ অর্থাৎ খোজাদের শাস্ত্ৰ-গ্ৰন্থ থেকে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু এবারে যেটি বলব সেটি আমার শোনা গল্প-এক নাস্তিক খোজার কাছ থেকে।
একদিন নাকি খানা খেতে খেতে পঞ্চম জর্জ আগা খানকে জিজ্ঞেস করেন, ‘এ কথা কি সত্যি, ইয়োর হাইনেস, যে, আপনার চেলারা আপনাকে পুজো করে?’
আগা খান নাকি উত্তরে বলেছিলেন, ‘তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে, ইয়োর ম্যাজেস্টি? মানুষ কি গোরুকেও পুজো করে না?’
উত্তরটার দর আমি আর যাচাই করলুম না।
এ তো মেয়ে মেয়ে নয়…–
সংবাদপত্রের পাঁজে যাঁরা পোড় খেয়ে ঝামা হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত আত্মজনের মৃত্যুতেও বিচলিত হন না। হবার উপায়ও নেই। কারণ, যদি সে আত্মজন প্রখ্যাতনামা পুরুষ হন, তবে সাংবাদিককে অশ্রু সংবরণ করে সে মহাপুরুষ সম্বন্ধে রচনা লিখতে বসতে হয়। এ অধম পাঁজাতে ঢুকেছে বটে, পোড়ও খেয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঝামা হয়ে যায় নি বলে তার চোখের জল মুছতে অনেকখানি সময় কেটে গিয়েছে।
বহু সাহিত্যিক, বহু কবি, বহু ঔপন্যাসিকের সঙ্গে দেশবিদেশে আমার আলাপ হয়েছে কিন্তু সরোজিনী নাইডুর মত কলহাস্যমুখরিত, রঙ্গরসে পরিপূর্ণ অথচ জীবনের তথা দেশের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য সম্বন্ধে সচেতন দ্বিতীয় পুরুষ বা রমণী আমি দেখি নি। কতবার দেখেছি দেশের গভীরতম দৈন্য-দুৰ্দশা নিয়ে গভীরভাবে, তেজীয়ান ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি রঙ্গরসে চলে গিয়েছেন। লক্ষ্য করে তখন দেখেছি যে, রসিকতার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু তখনও চোখের জল ছলছল করছে। আমার মনে হয়েছে, দুঃখ-বেদনার কথা বলতে বলতে পাছে তিনি সকলের সামনে হঠাৎ কেঁদে ফেলেন, সেই ভয়ে কথার বাঁক ফিরিয়ে হাসি তামাসায় নেমে পড়েছেন।
চটুল রসিকতাই হোক আর গুরুগম্ভীর রাজনীতি নিয়েই কথা হোক, সরোজিনী যে ভাষা যে শৈলী ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন কোন সাহিত্যিক বা কবির নাম মনে পড়ছে না। রবীন্দ্ৰনাথ গল্প বলতে অদ্বিতীয় ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সরোজিনীর মত কখনও শতধা উচ্ছসিত হতেন না। সরোজিনী আপন-ভোলা হয়ে দেশকলপোত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যে গল্পগুজব করে যেতেন, তাতে মজলিস জমত ঢের বেশি। রবীন্দ্রনাথ যেমন কখনও কাউকে খুব কাছে আসতে দিতেন না, সরোজিনীর মজলিসে কারো পক্ষে দূরে বসা ছিল অসম্ভব।
এরকম প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন অল্প লোক। অথচ সরোজিনীর চেয়ে অল্প প্রতিভা নিয়ে অনেকেই সরোজিনীর চেয়ে সফলতর সৃষ্টিকার্য করতে সক্ষম হয়েছেন। সরোজিনীর ভাব গম্ভীর ছিল, ভাষা মিষ্ট ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁর কাব্য-সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার পিছনে পড়ে রইল কেন?
আমার মনে হয়, সরোজিনীকে যাঁরা বক্তৃতা দিতে শুনেছেন, তাঁর মজলিসে আসন পাবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তারাই স্বীকার করবেন বিদেশী মায়ামৃগের সন্ধানে বেরিয়ে সরোজিনী স্থায়ী যশের সতী সীতাকে হারালেন। এতে অবশ্য সরোজিনীর দোষ নেই। অল্প বয়সে তিনি যে ভাষা শিখেছিলেন, পরিণত বয়সে সেই ভাষাতেই তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু মাতৃস্তন্য না খেয়ে তিনি হরলিকস্ খেয়েছিলেন বলে তাঁর কবিতা কখনও মাতৃরসের স্নিগ্ধতা পেল না। আমি জানি পৃথিবীতে আজ ইংরেজ ছাড়া কোনো বিদেশী সরোজিনীর মত ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখতে পারবেন না। এ বড় কম কথা নয়, কিন্তু এ কৃতিত্বও আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। কারণ নিশ্চয় জানি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি দ্বন্দ্বের বাতাবরণে যদি সরোজিনী বাল্যকাল না কাটাতেন, বাংলা মায়ের কোলে বসে যদি তিনি শুধু বাংলাই শুনতেন, তা হলে কৈশোরে বিদেশী ভাষা তার কবিত্ব-প্রতিভাকে ভস্মাচ্ছাদিত করতে পারত না-মাইকেলের প্রতিভা যে রকম বিদেশী ভস্মকে অনায়াসে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল। তাই সরোজিনী আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন। সরোজিনী প্রমাণ করে দিলেন, বিদেশী ভাষায় কখনও স্থায়ী সৃষ্টি-কর্ম সম্ভবপর হয় না। আর কোনো ভারতবাসী ভবিষ্যতে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে কবিতা লিখবে না। পূর্ব-পাকিস্তান উর্দু গ্ৰহণ না করে বিচক্ষণের কার্য করছে। পশ্চিমবঙ্গ যেন হিন্দি-মৃগের সন্ধানে না বেরোয়।
পাঠক যেন না ভাবেন, আমি সরোজিনীর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হইনি। আমি শুধু বলতে
কবির মত অবসর সময়ে কবিতা লিখে বাদবাকি সময় সাধারণ লোকের মতন কাটাতেন না। তাঁর কথা, তার হাসি, তার গালগল্প, তাঁর রাগ, তার অসহিষ্ণুতা, তার ধৈৰ্য্যচুতি, তার আহার বিহার ভ্রমণ বিলাস সব কিছুই ছিল কবিজনেচিত। রাজনৈতিক সরোজিনী, জনপদকল্যাণী সরোজিনী বাকনিপুণা সরোজিনী-এই তিন এবং অন্য বহুরূপে যখন তিনি দেখা দিতেন, তখন সেসব রূপই তার কবিরূপের নীচে চাপা পড়ে যেত। কবিতা রচয়িত্রী সরোজিনীর চেয়েও কবি সরোজিনী বহু বহু গুণে মহত্তর।
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলার এক কবি লিখেছিলেন বাংলার কুঁড়েঘরে রবির উদয় হল, এ বিস্ময় আমাদের কখনও যাবে না। ঠিক তেমনি ভারত এমন কি পুণ্য করেছিল যে তার বুকে ফুটে উঠল সরোজিনী?
এষাস্য পরমাগতি
প্রাচ্যভূমি থেকে শ্বেতের প্রাধান্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নব নব আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতির ভূমিতেও নূতন নূতন চাষ-আবাদ আরম্ভ হয়েছে। চীনদেশ থেকে আরম্ভ করে ইন্দোনেশিয়া, ভারত-পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্থান, ইরান, আরব ভূমি পেরিয়ে একদিকে মরক্কো পর্যন্ত এবং অন্য দিকে তুর্কী ইস্তক। সবগুলোর খবর রাখা অসম্ভব-এতগুলো ভাষা শেখার শক্তি এবং সময় আছে কার?–তবু মোটামুটিভাবে তার খানিকটা জরিপ করা যায়।
তিনটে বড় বড় বিভাগ করে প্রাথমিক জরিপ করা যায়। চীন, ভারত, পাকিস্তান এবং আরব ভূমি। ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং তুর্কীকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু উপস্থিত সেগুলোকে হিসেবে নিলে আলোচনাটা একদম কিন্তুজার বাইরে চলে যাবে।
এ তিন ভূখণ্ডেই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতির বাজারে দিশী-বিদেশী দুই মালই চলছে। দর্শন, বিজ্ঞানের তুলনায় সাহিত্যই উপস্থিত এ তিন ভূখণ্ডে সংস্কৃতির প্রধান বাহন—এবং সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি যে বস্তু লেখা এবং পড়া হচ্ছে সে হল উপন্যাস এবং ছোট গল্প। এ দুই জিনিসই প্ৰাচ্যদেশীয় নিজস্ব ঐতিহ্যগত সম্পদ নয়; ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজের কাছ থেকে শেখা। চিত্র-ভাস্কৰ্য-স্থাপত্যের বেলাও তাই-সেজান, রেনওয়া, রিদাঁ এপস্টাইনের প্রভাব কি কাইরো কি কলকাতা সর্বত্রই দেখা যায়। ইয়োরোপীয় দর্শন এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে সবচেয়ে বেশি। মাথা ঘামাচ্ছে ভারত-কিছুটা কাইরো, তেলাভিভ এবং বাইরুত। একমাত্র ওস্তাদী সঙ্গীতের বেলা বলা যেতে পারে যে, ইয়োরোপীয় প্রভাব এর উপর কোন চাপই দিতে পারে নি।
কিন্তু এরকম পদ গুনে গুনে ফিরিস্তি বানাতে গেলে একখানা ছোটখাটো বিশ্বকোষ লিখতে হয়। সেটা এড়াতে হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়।
বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি নির্মিত হয়। বিশেষ মনোবৃত্তি হৃদয়াবেগ দ্বারা। তার কিছুটা হদিস পেলে মোটামুটিভাবে বলতে পারা যায়, বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি চলছে কোন পথে।
শ্বেতের প্রভাব কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে আন্দোলন এ তিন ভূখণ্ডে গাঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে ছুৎবাই’, ‘বিশুদ্ধীকরণ’ বা সত্যযুগে প্রত্যাবর্তন’ নাম দেওয়া যেতে পারে। এর প্রধান ধর্ম, বৈদেশিক সর্বপ্রকার প্রভাব বর্জন করে বিশেষ কোন প্রাচীন ঐতিহ্যকে নূতন করে চাঙ্গা করে তোলা। এই ভারতবর্ষেই কেউ চায় বৈদিক যুগে ফিরে যেতে (ক্রিয়াকাণ্ডে যাদের ভক্তি অত্যধিক), কেউ চায় উপনিষদের যুগ জাগাতে (দার্শনিক মনোবৃত্তিওয়ালারা), কেউ বা গুপ্ত যুগ (সাহিত্য-কলায় যাদের মোহ), কেউ বা ভক্তি যুগে (বৈষ্ণবজন) ডুব মারতে চান। কেউ বলেন, রবারের জুতো পরে কাঁচা শাকসব্জি খাও, কেউ বলেন, ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশি মেলামেশি করছে, তাদের সিনেমা যেতে বারণ করে দাও। পাকিস্তানে এ আন্দোলন ইসলামী রাষ্ট্রের নামে শক্তি সঞ্চয় করতে চায়। কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কট্টর মৌলানারা এ-দলেরই শামিল। ইন্দোনেশিয়ায় এদেরই নাম দার-উলইসলাম সম্প্রদায়। ইবন ইসউদ গোষ্ঠীর ওয়াহহাবী আন্দোলন এই মনোবৃত্তি নিয়েই আরম্ভ হয়। এ-দলের মান্দারিনরা চীনে কিন্তু বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না।
প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বানচাল হবে। তার প্রধান কারণ, কোন দেশেরই যুবক সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী হচ্ছে না।
দ্বিতীয় আন্দোলন ঠিক এর উল্টো। এর চাঁইরা বলেন, ‘প্ৰাচ্য প্ৰাচ্য করে তো ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজের হাতে মার খেলে বিস্তর। প্ৰাচ্য ঐতিহ্য সর্বপ্রকার প্রগতির ‘এনিমি নাম্বার ওয়ান’। আমাদের সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি প্রচেষ্টা যদি আধুনিকতম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে বিজড়িত না হয়, তবে তার কোন প্রকারেরই ভবিষ্যৎ নেই।’ এ আন্দোলনের বড় কর্তাদের অধিকাংশই কমুনিস্ট ভায়ারা। এঁদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের রঙঢং সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিত্তোৎপাদন এবং ধন-বন্টন পদ্ধতির উপর এবং যেহেতু প্রাচ্যভূমিও একদিন মার্কসের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুযায়ী প্রলেতারিয়ারাজে পরিণত হবে, সেই হেতু প্রাচ্যেরও সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণ-নৃত্য, গণনাট্য, গণ-সাহিত্যের উপর। তাই ঐতিহ্যগত সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি ‘বুর্জুয়া’–সুতরাং বৰ্জনীয়।
ভারত-পাকিস্তানে এ আন্দোলন সুবিধে করে উঠতে পারছে না, কিন্তু বিশেষ করে তুর্কীতে এবং কিছুটা কাইরো বাইরুতে এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কমুনিস্ট ছাড়াও বহু যুবক-যুবতী এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই যে প্রথম আন্দোলনে যোগ দিতে হলে ক্ল্যাসিকস পড়তে হয়, সঙ্গীতের শখ থাকলে দশ বছর সা রে গা মা করতে হয়, কুরানহাদিস কণ্ঠস্থ করতে হয়-তাতে বায়ানাঙ্কা বিস্তর। এতো হাঙ্গামা পোয়ায় কে? তাই দ্বিতীয়টাই সই।
এ দুই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন টুমান স্তালিন। আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।
তৃতীয় আন্দোলন প্রাচ্যভূমিতে আরম্ভ করেন রাজা রামমোহন। তাঁর প্রচেষ্টা বাঙালী পাঠককে নূতন করে বলতে হবে না। প্রাচ্যভূমির ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ মিলিয়ে নিয়ে তিনি নব নব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ তাদের স্বপ্নকে বৈদগ্ধ্যের বহু ক্ষেত্রে মূর্তমান করেছেন। কাইরের তাহা হোসেন, বাইরুতের খলীল গিবরানী, ঢাকার বাঙালী সাহিত্যিক সম্প্রদায়, লাহোরে ইকবালের শিষ্যমণ্ডলী এবং ইন্দোনেশিয়ার সুতান শহরীর এ সম্প্রদায়ভুক্ত।
বিশেষ করে সুতান শহরীরের নাম ভক্তি ভরে স্মরণ করতে হয়। জাভা সুমাত্রা বালীর অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সদানন্দ কৃত্রিমতা বিবর্জিত সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ান এতদিন ধরে গড়ে উঠেছে, ওলন্দাজ বর্বরতা যাকে বিনষ্ট করতে পারে নি, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে শহরীর চান উত্তম উত্তম ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভব সম্পদ যোগ দিয়ে নূতন সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। এবং সে চাওয়ার পিছনে রয়েছে শরীরের নিরঙ্কুশ আত্মত্যাগ আর কঠোরতম সাধনা। বিশ্বসংসারের সব আন্দোলন সব প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি নিজেকে অহরহ সংযুক্ত রেখে সেই পন্থার অনুসন্ধান করছেন, যে পন্থা শুধু যে ইন্দোনেশিয়ার চিন্তাবিকাশ কলাপ্রকাশ মূর্তমান করবে। তাই নয়, তাবৎ প্রাচ্যভূমি তার থেকে অনুপ্রেরণা আহরণ করতে পারবে।
এ পন্থা অন্বেষণে নিজেকে অহরহ সজাগ রাখতে হয়-গীতার সংযমী, যিনি সদাজাগ্ৰত তিনিই এ মার্গের অধিকারী। শহরীর এ মার্গের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।
এষাস্য পরমাগতি।
কালো মেয়ে
কত করুণ দৃশ্য, কত হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখি প্রতিদিন—সত্য বলতে কি, তাই রাস্তায় বেরুতে ইচ্ছে করে না—কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, সব চেয়ে মর্মদ্ভদ আমার কাছে কি লেগেছে, তবে বলব, আমাদের পাড়ার কালো মেয়েটি।
সকালবেলা কখন বেরিয়ে যায় জানি নে। সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফেরে—আমি তখন রকে বসে চা খাচ্ছি। মাথা নিচু করে, ক্লান্ত শ্লথগতিতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত আমাদের রকের দিকে একবারও ঘাড় তুলে তাকায়নি-আমার মনে হয়, এ জীবনে কোনোদিনই সে কোনো দিকে তাকিয়ে দেখে নি।
দেবতা ওকে দয়া করেন নি। রঙ কালো এবং সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই— কেমন যেন ছাতা-ধরা-মসনে-পড়া ছাবড়া-ছাবড়া। গলার হাড় দুটি বেরিয়ে গিয়ে গভীর দুটো গর্ত করেছে, গায়ের কোথাও যেন একরাত্তি মাংস নেই, গাল ভাঙা, হাত দুখানা শরের কাঠি, পায়ে ছেড়াচপ্পল, চুলে কতদিন হল তেল পরে নি কে জানে! আর সমস্ত মুখে যে কী বিষাদ আর ক্লান্তি তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা আমার নেই। শুধু জানি-স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি-দিনের পর দিন তার মুখের বিষাদ আর ক্লান্তি বেড়েই চলেছে। আরো জানি একদিন তাকে আর দেখতে পাবো না। শুনবো, যক্ষ্মা কিংবা অন্য কোনো শক্ত ব্যামোয় পড়েছে, কিংবা মরে গিয়েছে।
শুনলুম মাস্টারনীগিরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে। তার নাকি পয়সাওলা এক দাদাও আছে–সে থাকে অন্যত্র বউ নিয়ে, এদের দিকে তাকায় না।
বাপ দাদা করেছিলেন। তাই আমিও ভগবানে বিশ্বাস করি গতানুগতিকতাকে, কিন্তু যদি এ মেয়ের কোনদিন বর জোটে। তবেই ভগবানে আমার সত্যকার বিশ্বাস হবে।
জানি না জানি, এর চেয়েও অনেক বেশি নিদারুণ জিনিস সংসারে আছে, কলকাতাতেই আছে। কিন্তু আমি পাড়াগেয়ে ছেলে, মেয়েছেলে নিষ্ঠুর সংসারে লড়াই করে অপমান-আঘাত সহ্য করে টাকা রোজগার করে, এ জিনিস দেখা আমার অভ্যাস নেই, কখনো হবে না। গাঁয়ের মেয়েও খাটে-আমার মাও কম খাটতেন না—কিন্তু তাঁর খাটুনি তো বাড়ির ভিতরে। সেখানেও মান-অপমান দুঃখ-কষ্ট আছে স্বীকার করি,-কিন্তু এই যে পাড়ার কালো মেয়েটি, যে সকল হতে না হতেই নাকে-মুখে দুটি গুঁজে, এর কনুই, ওর হাঁটুর ধাক্কা খেয়ে ট্রামে-বাসে উঠছে, দুপুর বেলা কিছু খাবার জুটবে না, জুটবে হয়তো হেড মিসট্রেসের নির্মম ব্যবহার, ছাত্রীদের অবজ্ঞা অবহেলা-হয়তো তার শ্ৰীহীনতা নিয়ে দুএকটা হৃদয়হীন মন্তব্যও, তাকে শুনতে হয়। ক্লাস শেষ হলে সে খাতা দেখতে আরম্ভ করবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় যখন ক্ষুদে লেখা পড়বার চেষ্টায়। গর্তে-ঢোকা চোখ দুটো ফেটে পড়বার উপক্রম করবে। তখন উঠবে বাড়ি ফেরার জন্য। আজ হয়তো বাসের পয়সা নেই, বাড়ি ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে। ক’মাইলের ধাক্কা আমি জানি নে।
কিন্তু জানি, আমি যে গ্রামে জন্মেছি, সেখানে এককালে সব মেয়েরই বর জুটত। ভালো হোক, মন্দ হোক জুটত এবং ছোট হোক, বড় হোক কোনো না কোনো সংসারে গিয়ে সে আশ্রয় পেত।
আজ আর সেদিন নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের কটি ছেলে আজ পয়সা কামাতে পারে যে বিয়ে করবে? এককালে গ্রামে সকলেরই দুমুঠো অন্ন জুটত—তা সে গতির খাটিয়ে, চাকরি করেই হোক, আর না করেই হোক।–তাই শেষ পর্যন্ত শ্ৰীহীনা মেয়েরও বর জুটত। আজ যে দু-চারটি ছেলে পয়সা কামাবার সুযোগ পায়, তারা কনের বাজারে ঢুকে বেছে নেয় ডানাকাটা পরীদের। সাধারণ মেয়েরাও হয়ত বর পায়, শুধু শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকে আমাদের পাড়ার মাস্টারনী আর তারই মত মলিনারা।
এ সমস্যা যে শুধু আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়। বেকার-সমস্যা যেখানে থাকবে সেখানেই, ছেলেরা বিয়ে করতে নারাজ। মেয়েরাও বুঝতে পারে, বর পাবার সম্ভাবনা তাদের জীবনে কম, তাই তারাও কাজের জন্য তৈরি হয়–বাপ-মা তো একদিন মারা যাবেন, দাদারা তাকে পুষতে যাবে কেন? এই একান্ন পরিবারের দেশেই দাদারা ক্রমশ সরে পড়ছে, যে দেশ। কখনো একান্ন পরিবার ছিল না। সেখানে অরক্ষণীয়াকে পুষিবে কে? কিন্তু আর আর দেশ আমাদের মত মারাত্মক গরিব নয় বলে টাইপিস্ট মেয়েটির পেট-ভরা অন্ন জোটে, মাস্টারনী যখন বাড়ি ফেরে তখন তার মুখে ক্লান্তি থাকলেও মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার যাবার মত পয়সা সে কামায়ও বটে। বর জুটবে না, মা হতে পারবে না, সে দুঃখ তার আছে, কিন্তু ইয়োরোপের মেয়ের অনেকখানি স্বাধীনতা আছে বলে প্রেমের স্বাদ কিছুটা পায়। নৈতিক উচ্ছঙ্খলতার নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয় : এ দেশের মেয়েরা পরিণয়বন্ধনের বাইরে প্রেমের সন্ধানে ফিরুক, এ কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই, পশ্চিমের অরক্ষণীয়া তবু কোনো গতিকে বেঁচে থাকার আনন্দের কিছুটা অংশ পায়-আমাদের পাড়ার মেয়েটি যে এ জীবনে কোনো প্রকার আনন্দের সন্ধান পাবে সে দুরাশা আমি স্বপ্নেও করতে পারি নে। এ মেয়ের দুরবস্থার জন্য দায়ী কে? আমি সোজাসুজি বলবো, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক কর্তারা। পাঠক জানেন, এ অধম সপ্তাহের পর সপ্তাহ লিখে যাচ্ছে, কিন্তু কারো নিন্দে সে কখনো করতে যায় নি। সে চেষ্টা করেছে। আপনাদের আনন্দ দিতে-তারই ফাঁকে ফাঁকে যে সপ্তাহে সে তত্ত্ব বা তথ্য পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়েছে, সেদিন তার আনন্দের অবধি থাকে নি; এর গলদ, ওর ক্রটি নিয়ে সে আলোচনা বা গালাগালি করে কোনো সস্তা রুচিকে সে টক-ঝাল দিয়ে খুশি করতে চায় নি। কিন্তু এখন যদি না বলি যে আমাদের কর্তারা আজ পর্যন্ত দেশের অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করতে পারেন নি, কোনো পরিকল্পনা পর্যন্ত করতে পারেন নি, তা হলে অধৰ্মাচার হবে। বেকার-সমস্যা ঘোচাতে পারুন আর নাই পারুন, মধ্যবিত্তকে অন্ন দিতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত তারা যেন তরুণ-তরুণীদের মনে একটুখানি আশার সঞ্চার করে দিতে পারেন। ভালো করে ভাত না জুটলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, যদি তার মনে আশা উদ্দীপ্ত করে দেওয়া যায়।
আমাদের কালো মেয়ের কোনো ভবিষ্যৎ নেই—এ কথা ভাবতে গেলে মন বিকল হয়ে যায়-কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়েই চলবে, এ কথা ভাবলে কর্তাদের বিরুদ্ধে সর্বন্দেহমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।
আশাটুকুরও সঞ্চার যদি কর্তারা না করতে পারেন, তবে তারা আসন ত্যাগ করে সরে পড়েন না কেন? হায়, অরক্ষণীয়ার অভিসম্পাতকেও এরা আর ভয় করেন না!
কিংবদন্তীচয়ন
রিয়োকোয়ান প্রকৃতি আর ছেলেপিলেদের নিয়েই বেশির ভাগ জীবন কাটিয়েছেন। ফিশার বলেন, তিনি কোনো জায়গাতেই কিছুদিন থাকলেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে চিনে নিত। ফিশার বলেন নি। কিন্তু আমরা দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃতি তাকে চিনে নিত এবং রবীন্দ্রনাথের ‘হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহে নি কথা’ কবিতাটি আমরা মতের সায় দেবে।
রিয়োকোয়ান গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় ছেলেমেয়রা লুকোচুরি খেলছিল। রিয়োকোয়ানকে দেখে তাদের উৎসাহ আর অনন্দের সীমা নেই। বেশি ঝুলো বুলি করতে হল না। রিয়োকোয়ান তো নাচিয়ে বুড়ি, তার উপর পেয়েছেন। মৃদঙ্গের তাল। তদণ্ডেই খেলাতে যোগ দিলেন। খেলোটা বনের ভিতর ভালো করে জমবে বলে সবাই গ্রাম ছেড়ে সেখানে উপস্থিত। সবাই হেথায় হোথায় লুকোলো। রিয়োকোয়ান এ খেলাতে বহু দিনের অভ্যাসের ফলে পাকাপোক্ত-তিনি লুকোলেন এক কাঠুরের কুঁড়েঘরে। ঘরের এক কোণে কাঠ গাদা করা ছিল, তিনি তার উপরে বসে ঝোলা-ঝোলা আস্তিন দিয়ে মুখ ঢেকে ভাবলেন, ওখানে তাকে কেউ ককখনো খুঁজে পাবে না, আর পেলেই বা কি, তার তো মুখ ঢাকা, চিনবে কি করে?
খেলা চলল। সবাইকে খুঁজে পাওয়া গেল। রিয়োকোয়ান যে কুঁড়েঘরে লুকিয়েছিলেন, সে-কথা কারো অজানা ছিল না, কিন্তু ছেলেরা বলল, ‘দেখি, আমরা সবাই চুপচাপ বাড়ি চলে গেলে কি হয়?’
রিয়োকোয়ান সেই কাঠের গাদার উপর বসে সমস্ত বিকেল বেলাটা কাটালেনপরদিন সকাল বেলা কাঠুরের বউ ঘরে ঢুকে চমকে উঠে বলল, ‘ওখানে কে ঘুমুচ্ছ হে?’ তার পর চিনতে পেরে ‘থ’ হয়ে বলল, ‘সে কি, সন্ন্যাসী ঠাকুর যে! আপনি এখানে কি করছেন?’
রিয়োকোয়ান আস্তিন-পাস্তিন নাড়িয়ে মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘আরো চুপ, চুপ, চুপ। ওরা জেনে যাবে যে। বুঝতে পারো না!’
‘চলো’ খেলা
রিয়োকোয়ানকে যে ছেলেমেয়ের হামেশাই বোকা বানাতে পারত, সে-কথা সবাই জানে, আর পাঁচ জনও তাকে আকসার ঠকাবার চেষ্টা করত। কিন্তু প্রশ্ন, রিয়োকোয়ানের কাছে এমন কি সম্পদ ছিল যে মানুষ তাকে ঠকাবার চেষ্টা করবে? ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা ছবির চেয়েও বেশি কদর পেত এবং সেই হাতের লেখায় তাঁর কবিতার মূল্য অনেক লোকই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু রিয়োকোয়ান চট করে যাকে-তাকে কবিতা দিতে রাজী হতেন না, বিশেষ ক্রএ যারা তাঁর কবিতা বিক্রি করে পয়সা মারার তালে থাকত, তাদের ফন্দী-ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা সব সময়ই করতেন। গল্পগুলো থেকে জানা যায়, তিনি ফাঁদে ধরা পড়েছেনই বেশি, এড়াতে পেরেছেন মাত্র দু-এক বার।,
জাপানে চলো’ খেলার খুবই চলতি, আর রিয়োকোয়ানকে তো কোন খেলাতেই নামাবার জন্য অত্যধিক সাদাসাদি করতে হত না।
রিয়োকোয়ান বন্ধু মনসুকের সঙ্গে একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন। মনসুকে বললেন, ‘এসো, ‘চলো’ খেলা খেলবে? রিয়োকোয়ান তো তৎক্ষণাৎ রাজী। মনসুকে খেলা আরম্ভ করার সময় বললেন, ‘কিছু একা বাজি ধরে খেললে হয় না? তাহলে খেলোটা জমবে ভালো ।’
রিয়োকোয়ান বলেন, ‘তা তো বটেই। যদি আমি জিতি তাহলে তুমি আমাকে কিছু কাপড়-জমা দেবে-শীতটা তো বেড়েই চলেছে।’
মনসুকে বললেন, ‘বেশ, কিন্তু যদি আমি জিতি?’
রিয়োকোয়ান তো মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন। তাঁর কাছে আছেই বা কি, দেবেনই বা কি? বললেন, ‘আমার তো, ভাই, কিছুই নেই।’
মনসুকে অতি কষ্টে তাঁর ফুর্তি চেপে বললেন, ‘তোমার চীনা হাতের লেখা যদি দাও তাইতেই আমি খুশি হব।’ রিয়োকোয়ান অনিচ্ছায় রাজী হলেন। খেলা আরম্ভ হল। রিয়োকেয়ান হেরে গেলেন। আবার খেলা শুরু আবার রিয়োকোয়ানের হার হল। করে করে সবসুদ্ধ আট বার খেলা হল, রিয়াকোয়ান আট বারই হারলেন। আর চীনা হাতের লেখা না দিয়ে এড়াবার যো নেই।
রিয়োকোয়ান হস্তলিপি দিলেন। দেখা গেল, আটখানা লিপিতেই তিনি একই কথা আট বার লিখেছেন :
‘চিনি মিষ্টি
ওষুধ তেতো।’(১)
মনসুকে যখন আপত্তি জানিয়ে বললেন, আট বার একই কথা লেখা উচিত হয় নি তখন রিয়োকোয়ান হেসে উত্তর দিলেন, ‘কিন্তু ‘চলো’ খেলা কি সব বারই একই রকমের হয় না? তাই একই কথা আট বার লিখে দিয়েছি।’
কুড়িয়ে-পাওয়া
রিয়োকোয়ানকে কে যেন এক বার বলেছিল রাস্তায় পয়সা কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী আনন্দ। একদিন আশ্রমে ফেরার পথে তিনি মনে মনে সেই কথা নিয়ে চিন্তা করতে করতে বললেন, ‘একবার দেখাই যাক না, কুড়িয়ে পাওয়াতে কি আনন্দ লুকনো আছে।’ রিয়োকোয়ান ভিক্ষা করে কয়েকটি পয়সা পেয়েছিলেন। সেগুলো তিনি একটা একটা করে রাস্তায় ছড়িয়ে ফের তুলে নিলেন। অনেকবার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন রকম আনন্দই পেলেন না। তখন মাথা চুলকে আপন মনে বললেন, ‘এটা কি রকম হল? আমায় সবাই বললে, কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী ফুর্তি, কিন্তু আমার তো কোন ফুর্তি হচ্ছে না। তারাও তো ঠকাবার লোক নয়।’ আরো বহু বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন সুখই পেলেন না। এই রকম করতে করতে শেষটায় বেখেয়ালে সব কটি পয়সাই ঘাসের ভিতর হারিয়ে গেল।
তখন তাকে অনেকক্ষণ ধরে পয়সাগুলো খুঁজতে হল। যখন পেলেন তখন মহা ফুর্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, ‘এইবারে বুঝতে পেরেছি। কুড়িয়ে পাওয়াতে আনন্দ আছে বৈকি।’
ধূর্ত নাপিত
রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা এতই সুন্দর ছিল আর তাঁর কবিতাতে এমনি অপূর্ব রসসৃষ্টি হত যে তাঁর হাতের লেখা কবিতা কেউ যোগাড় করতে পারলে বিক্রি করে বেশ দুপিয়সা কামাতে পারত। রিয়োকোয়ান নিজে শ্রমণ; কাজেই তিনি এসব লেখা বিক্রি করতেন না— গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু কেউ ধাপ্পা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করার চেষ্টা করলে তিনি ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা করতেন।
শ্রমণকে মাথা নেড়া করতে হয়। তাই রিয়োকোয়ান প্রায়ই এক নাপিতের কাছে যেতেন। নাপিতটি আমাদের দেশের নাপিতের মতই ধূর্ত ছিল এবং রিয়োকোয়ানের কাছ থেকে অনবরত কিছু লেখা আদায় করার চেষ্টা করত। তাঁকে তাই নিয়ে বড্ড বেশি। জ্বালাতন করলে তিনিও ‘দেব দিচ্ছিা করে কোন গতিকে এ অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করতেন।
শেষটায় ধূর্ত নাপিত একদিন তাঁর মাথা অর্ধেক কামিয়ে বলল, ‘ঠাকুর, হাতের লেখা ভালোয় ভালোয় এই বেলা দিয়ে দাও। না হলে বাকী অর্ধেক আর কামাবো না।’ এ-রকম শয়তানির সঙ্গে রিয়োকোয়ানের এই প্রথম পরিচয়। কি আর করেন? হাতের লেখা দিয়ে। মাথাটি মুড়িয়ে—উভয়ার্থে-আশ্রমে ফিরলেন। নাপিতও সগর্বে সদম্ভে লেখাটি ফ্রেমে বঁধিয়ে দোকানের মাঝখানে টাঙালো-ভাবখানা এই সে এমনি গুণী যে রিয়োকোয়ানের মত শ্ৰমণ তাকে হাতের লেখা দিয়ে সম্মান অনুভব করেন।
কিন্তু খদ্দেরদের ভিতর দু’চারজন প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তাঁরা নাপিতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, লেখাতে একটা শব্দ সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গিয়েছে। নাপিত ছুটে গিয়ে রিয়োকোয়ানের ভুল দেখিয়ে শুদ্ধ করে দেবার জন্যে বলল। তিনি বললেন, ‘ওটা ভুল নয়। আমি ইচ্ছে করেই ও রকম ধারা করেছি। তুমি আমার অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছিলে। আমিও তাই লেখাটি শেষ করে দিইনি। আর ঐ যে বুড়ি আমাকে সিম বিক্রি করে সে সর্বদাই আমাকে কিছুটা ফাউ দেয়। তোমার লেখা লেখায় যেটুকু বাদ পড়েছে সেটুকু বুড়িকে লেখা দেবার সময় ফাউ করে জুড়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখে এসো।’
তার পর রিয়োকোয়ান অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে হাসলেন।
রিয়োকোয়ান ও মোড়ল তোমিতোরি
শ্রমণদের দিন কাটে নানা ধরনের লোকের আতিথ্য নিয়ে। রিয়োকোয়ান একবার অতিথি হলেন মোড়ল তোমিতোরির। জাপানে তখন চলো’ খেলার খুব চলতি এবং রিয়োকোয়ান সর্বদাই এ-খেলাতে হারেন বলে সকলেই তাঁর সঙ্গে খেলতে চায়।
তাই খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু রিয়োকোয়ানের অদৃষ্ট সেদিন ভালো ছিল। বাজীর পর বাজী। তিনি জিতে চললেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ভারী খুশি-রিয়োকোয়ানও আনন্দে আত্মহারা। তোমিতোরি রিয়োকোয়ানকে বিলক্ষণ চিনতেন, তাই রগড় দেখবার জন্য হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বললেন, ‘তুমি তো আচ্ছা লোক হে! অতিথি হয়ে এসেছ আমার বাড়িতে আর জিতে জিতে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিতে তোমার একটুকু লজ্জা হচ্ছে না? এরকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভদ্রত্ব কি করে বজায় রাখা যায়। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি নে।’
রিয়োকোয়ান রসিকতা না বুঝতে পেরে ভারী লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি কোনো গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন বন্ধু কেরার বাড়িতে। কেরা বন্ধুর চেহারা দেখেই বুঝলেন, কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলে, ‘কি করেছ, খুলে বলো।’ রিয়োকোয়ান বললেন, ‘ভারী বিপদগ্ৰস্ত হয়েছি। তোমিতোরির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কি যে করব ভেবেই পাচ্ছি নে। তুমি কিছু বুদ্ধি বাংলাতে পারো? তোমিতোরিকে যে করেই হোক খুশি করতে হবে।’
কেরা ব্যাপারটা শুনে তখনই বুঝতে পারলেন যে রিয়োকোয়ান রসিকতা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তিনিও চেপে গিয়ে দরদ দেখিয়ে বললেন, ‘তই তো! তা আচ্ছা, কাল তোমাকে তোমিতোরির কাছে নিয়ে গিয়ে মাপ চাইব।’
রিয়োকোয়ান অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।
পরদিন ভোরবেলা দুজনা মোড়লের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। রিয়োকোয়ান দোরের বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেরা ভিতরে গিয়ে যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে, এ-রকম ভাবে গভীর গলায় রিয়োকোয়ানের হয়ে তোমিতোরির কাছে মাপ চাইলেন। রিয়োকোয়ান উদ্বেগে কাতর হয়ে কান খাড়া করে শুনতে পেলেন তোমিতোরি তাকে মাপ করতে রাজী আছেন। তদণ্ডেই দুশ্চিন্তা কেটে গেল আর মহা খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ তোমিতোরির সামনে গিয়ে হাজিরা। তোমিতোরি প্রচুর খাতির যত্ন করে রিয়োকোয়ানকে বসালেন। রিয়োকোয়ানকে আর তখন পায় কে! খুশিতে সব কিছু বেবাক। ভুলে গিয়ে এক লহমার ভিতরেই বললেন, ‘এসো, ‘চলো’ খেলা আরম্ভ করা যাক।’
রিয়োকোয়ান এমনই সরল মনে প্রস্তাবটা করলেন যে সবাই হেসে উঠলেন। খেলা * আরম্ভ হল।
এবারও রিয়োকোয়ান জিতলেন।
কী বিপদ
তাঁকে বড় বিপদগ্ৰস্ত করত।
কথা নেই বার্তা নেই একদিন হঠাৎ একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল, ‘ঠাকুর, আমায় একটা রায়ো দাও (রায়ো মুদ্রার দাম প্রায় চার টাকার মত)।’
রিয়োকোয়ান তো অবাক। এক রায়ো? বলে কি? তাঁর কাছে দুগণ্ডা পয়সা হয় কি না। হয়।’
ছেলেরা ছাড়ে না। আরেকজন বলল, ‘আমাকে দুটো রায়ো দাও।’ কেউ বলে তিনটে, কেউ বলে চারটে। নিলামের মত দাম বেড়েই চলল। আর রিয়োকোয়ান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাত দুখানা মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে ভাবছেন অত টাকা তিনি পাবনে কোথায়?
যখন নিলাম দশ রায়ো পেরিয়ে গেল তখন তিনি হঠাৎ দড়াম করে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।
ছেলেরা তো এতক্ষণ নিলামের ফুর্তিতে মশগুল হয়ে ছিল। রিয়োকোয়ানকে হঠাৎ এরকম ধারা মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ভয়ে-ভয়ে কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, ‘ও ঠাকুর, ওঠে। এ-রকম করছ, কেন?’ কোনো সাড়াশব্দ নেই। আরো কাছে এগিয়ে এসে দেখে তার চোখ বন্ধ, সমস্ত শরীরে নড়া-চড়া নেই।
ভয় পেয়ে সবাই কনের কাছে এসে চেঁচাতে লাগল, ও ঠাকুর, ওঠে। ও-রকম ধারা করছ, কেন?’ তখন কেউ কেউ বলল, ‘ঠাকুর মারা গিয়েছেন।’ দু-চারজন তো হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলল।
যখন হট্টগোলটা ভালো করে জমে উঠেছে তখন রিয়োকোয়ান আস্তে আস্তে চোখ মেললেন। ছেলেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক, ঠাকুর তাহলে মারা যান নি। সবাই তখন তাঁর আস্তিন ধরে ঝুলোকুলি করে চেঁচাতে লাগল, ‘ঠাকুর মরে যান নি, ঠাকুর বেঁচে আছেন।’ রায়ের কথা সবাই তখন ভুলে গিয়েছে। কানামাছি খেলা আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।
ফিশার আরও বহু কিংবদন্তী উদ্ধৃত করে তাঁর পুস্তিকাখনি সর্বাঙ্গসুন্দর করে। তুলেছেন। সেগুলো থেকে দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিয়োকোয়ান বয়স্ক লোকের সংসৰ্গ ত্যাগ করে ক্রমেই ছেলে-মেয়ে, প্রকৃতি আর প্রাণজগৎ নিয়ে দিনযাপন করেছেন। কিংবদন্তীর চেয়ে রিয়োকোয়ানের কবিতাতে তাঁর এই পরিবর্তন চোখে পড়ে বেশি।
বস্তুত, রিয়োকোয়ানের জীবনী আলোচনার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় তার কবিতা পাঠ। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতা লিখেছেন এমনি হাস্কা তুলি দিয়ে যে তার অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।
কোনো প্রকৃত সমঝদার যদি এই গুরুভার গ্রহণ করেন তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখা সার্থক হবে।
মহাপরিনির্বাণ
ভিক্ষুণী তেইশ (তাইশিন) রিয়োকোয়ানের শিষ্যা ছিলেন সে-কথা এ জীবনীর প্রথম ভাগেই বলা হয়েছে। রিয়োকোয়ানের শরীর যখন তোহাত্তর বৎসর বয়সে জরাজীর্ণ তখন তিনি খবর পেলেন শ্রমণের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সংবাদ পেয়ে তেইশ গুরুর পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন।
সেই অবসন্ন শরীর নিয়ে শ্রমণ যে মধুর কবিতাটি রচনা করেছেন তার থেকে আমরা তার স্বর্শকাতর হৃদয়ের খানিকটা পরিচয় পাই
নয়ন আমার যার লাগি ছিল তৃষাতুর এত দিন
ভুবন ভরিয়া আজ তার আগমন
তারই লাগি মোর কঠোর বিরহ মধুর বেদনা ভরা
তারই লাগি মোর দিন গেল অগণন।
এত দিন পরে মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আজ
শাস্তি বিরাজে ঝঞা-মথিত ক্ষুব্ধ হৃদয়-মাঝি।
শেষ দিন পর্যন্ত তেইশ রিয়োকোয়ানের সেবা-সুশ্রুষা করেছিলেন। গুরুর মন প্ৰসন্ন রাখার জন্য তেইশা সব সময়ই হাসিমুখে থাকতেন, কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভিক্ষুণী কতটা কাতর হয়ে পড়েছিলেন ফিশার তার পুস্তকে সে বেদনার কিছুটা বৰ্ণনা দিয়েছেন।
শেষ মুহূর্ত যখন প্রায় এসে উপস্থিত তখনো রিয়োকোয়ান তাঁর হৃদয়াবেগ কবিতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন–
নলিনীর দলে শিশিরের মত মোদের জীবন, হায়–
শূন্যগর্ভ বাতাহত হয়ে চলিছে সুমুখ পানে।
আমার জীবন তেমন কাটিল, ভোর হয়েছে শেষ
কাঁপন লেগেছে আমার শিশিরে–চলে যাবে কোনখানে।
রিয়োকোয়ান শান্তভাবে শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুণী তেইশার নারী-হৃদয় যে কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল, সে-কথা তেইশার ঐ সময়ের লেখা কবিতাটি থেকে বোঝা যায় :-
গভীর দুঃখ হৃদয় আমার সান্ত্বনা নাহি মানে
এ মহাপ্রয়াণ দুৰ্দমনীয় বেদনা বক্ষে হানে।
সাধনায় জানি, জীবন মৃত্যু প্ৰভেদ কিছুই নেই
তবুও কাতর বিদায়ের ক্ষণ সমুখে আসিল যেই।
এ কবিতা পড়ে আমাদের মত গৃহী একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে। সর্বস্ব ত্যাগ করে, আজীবন শাস্তির সন্ধান করার পরও যদি ভিক্ষুণীরা এ-রকম কথা বলেন তবে আমরা যাব কোথায়? আমরা তো আশা করেছিলুম, দুঃখের আঘাত সয়ে সয়ে কোনো গতিকে শেষ পর্যন্ত হয়ত আত্মজনের চিরবিচ্ছেদ সহ্য করার মত খানিকটা শক্তি পাব, কিন্তু তার আর ভরসা রইল কোথায়? ঋষি বলেছেন, ‘একমাত্র বৈরাগ্যেই অভয়’; কিন্তু তেইশার কবিতা পড়ে মানুষের শেষ আশ্ৰয় বৈরাগ্য সম্বন্ধেও নিরাশ হতে হল।
জানি, এ কবিতা পড়ে রিয়োকোয়ান উত্তরে লিখেছিলেন–
রক্তপদ্মাপত্রের মত মানব জীবন ধরে,
একে একে সব খসে পড়ে ভূমি ‘পরে
ঝরার সময় লাগে তার গায়ে যে ক্ষুদ্র কম্পন
সেই তো জীবন।
কিন্তু রিয়োকোয়ান তো ও-পারের যাত্রী–তাঁর দুঃখ কিসের? বিরহ-বেদনা তো তাদের তরেই, যারা পিছনে পড়ে রইল।
“–কিন্তু যারা পেয়েছিল প্ৰত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা?” (রবীন্দ্রনাথ)
তাই ফিশার বলেন, ‘শত শত লোক শ্রমণের সব-যাত্রার সঙ্গে গিয়েছিল। আর যেসব অগণিত ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তিনি খেলা-ধুলো করেছিলেন, তারাই যেন শ্রমণের শোকসন্তপ্ত বিরাট পরিবার।’
ফিশার তাঁর পুস্তিকা শেষ করেছেন রিয়োকোয়ানের সর্বশেষ কবিতাটি উদ্ধৃত করে,–
চলে যাবো যবে চিরতরে হেথা হতে
স্মৃতির লাগিয়া কী সৌধ আমি গড়ে যাবো কোন পথে?
কিন্তু যখন আসিবে হেথায় ফিরে ফিরে মধু ঋতু
পেলাব-কুসুম মুকুলিত মঞ্জরি
নিদাঘের দিন স্বর্ণ-রৌদ্রে ভরা
কোকিল কুহরে, শরৎ-পবন গান গায় গুঞ্জরি
রক্তপত্র সর্ব অঙ্গে মে’পল লইবে পরে
এরাই আমার স্মৃতিটি রাখিবে ধরে।
এরাই তখন কহিবে আমার কথা
ফুল্লকুসুম মুখর কোকিল যথা
রক্তবসনা দীপ্ত মে’পল শাখা
প্ৰতিবিম্বিত আমার আত্মা-এদেরই হিয়ায় আঁকা।
কোন গুণ নেই তার
বেহারী ভাইয়ারা (সদর্থে) বাংলা ভাষা এবং বাঙালির উপর খড়গহস্ত হয়েছেন শুনে বহু বাঙালি বিচলিত হয়েছেন। বাঙালির প্রতি অন্যান্য প্রদেশের মনোভাব যদি বাঙালিরা সবিস্তর জানতে পান তবে আরো বিচলিত হবেন—কিন্তু সৌভাগ্য বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, বাংলা দেশের লোক মারাঠী-গুজরাতী ভাষা নিয়ে অত্যধিক ঘাঁটাঘাঁটি করে না বলেই ও সব ভাষায় আমাদের সম্বন্ধে কি বলা হয় না হয়। সে সম্বন্ধে কোনো খবর পায় না। তাবৎ মারাঠী-হিন্দি-গুজরাতী আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু উত্তর-ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে ঈষৎ বাঙালি-বিদ্বেষ বর্তমান আছে সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই।
কিন্তু বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে বাংলা ভাষা তথা বাঙালি বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশ কেন যে ঈর্ষাপরায়ণ সে তত্ত্বের অনুসন্ধান করলে আমরা অনেকখানি ক্ষমা করতে পারব। ক্ষমা মহতের লক্ষণ তো বটেই, তদুপরি আমরা যখন সর্বপ্রদেশের মধ্যে প্রীতি এবং সৌহার্দ্য কামনা করি, তখন এ বিষয়ে আমাদেরই সকলের চেয়ে বেশি সচেতন হওয়া উচিত। আপন প্রদেশ সম্বন্ধে আমরাই যেমন সর্বপ্রথম গর্ব অনুভব করে ‘সপ্তকোটি কণ্ঠে’ উল্লাস্যধ্বনি করে উঠেছিলুম, ঠিক তেমনি আমরাই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বর্জন করে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল–বঙ্গের ভিতর দিয়ে ভারতভাগ্যবিধাতার রূপ দেখতে চেয়েছিলুম। আজ না হয়। বাংলাদেশ সর্বজনমান্য নেতার অভাবে অনাদৃত, আজ না হয় কেন্দ্ৰে আমরা চক্রবর্তী নেই, তাই বলে বাংলা দেশ আরো বহুকাল যে এরকম ধারা সর্বািযজ্ঞশালার প্রাস্তভূমিতে অনাদৃত থাকবে ও কথা বিশ্বাস করার চেয়ে আত্মহত্যা বহুগুণে শ্লাঘানীয়। তাই প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা দূর করার কর্তব্য আমাদেরই স্কন্ধে।
অবাঙালিরা যে বাঙালির দিকে বক্ৰদূষ্টিতে তাকান তার প্রধান কারণ এই নয় যে বাঙালি যেখানে যায়। সেখানকার হনুমানজী, রণঝোড়জী (আসলে ঋণছোড়জী অর্থাৎ যিনি মানুষকে সর্বপ্রকার ঋণমুক্ত করতে সাহায্য করেন) বা অম্বামীতার সেবা না করে কালীবাড়ি স্থাপনা করে কিংবা বিদ্যার্জন করবার জন্য গণপতিকে পুজো না করে সরস্বতীকে আহ্বান করে-কারণ সকলেই জানেন এ বাবদে তাবৎ ভারতবাসী একই গডডালিকার তাবেতে পড়েন। খুলে বলি।
বেদের ইন্দ্র, বরুণ, যম, প্রজাপতিকে দৈনন্দিন। ধৰ্মজীবন থেকে বাদ দিয়ে শুধু বাঙালিই যে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে তা নয়, ভারতবর্ষের কোনখানেই এদের জন্য আজ আর কোনো মন্দির নির্মিত হয় না। শিব আর বিষ্ণু কি করে যে এঁদের জায়গা দখল করে নিলেন সে আলোচনা উপস্থিত নিম্প্রয়োজন—অথচ বেদে এদের অনুসন্ধান করতে হয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে-এমন কবি বাঙালি যেমন সামাজিক ধৰ্মচর্চায় মা কালীকে ডাকাডাকি করে, উত্তর-ভারতে তেমনি হনুমানজী, গুজরাতে রণছোড়াজী, মহারাষ্ট্রে অম্বামীতা।
বেদনাটা সেখানে নয়। বাঙালির পয়লা নম্বরের ‘দোষ’ সে মাছ-মাংস খায়। কি উত্তর, কি দক্ষিণ-সর্বত্রই ব্ৰাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মাছ-মাংস খান না এবং উভয় বস্তুর খাদককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। মহারাষ্ট্রের সারস্বত ব্ৰাহ্মণগণ মাছ খান (এঁদের এক শাখার নাম গৌড়ীয় সারস্বত ও কিম্বদন্তী এই যে, তারা আসলে বাঙালি), তাই সেখানকার চিৎপবন, দেশস্থ এবং করাড় ব্রাহ্মণগণ সারস্বতদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন— যেন মাছ খেয়ে সারস্বত ব্ৰাহ্মণরা হিন্দু সমাজ থেকে ভ্ৰষ্ট হয়ে গিয়েছেন। এই মাছ খাওয়াটা দোষ না গুণ সে আলোচনা পণ্ডিত এবং বৈদ্যরাজ করবেন; উপস্থিত আমার বক্তব্য এই যে, মাছ-মাংস খায় বলেই বাঙালি সনাতন হিন্দুধর্মের কাছাকাছি থাকতে পেরেছে। নিরামিষে আসক্তি জৈন ধর্মের লক্ষণ-কারণ বৌদ্ধ গৃহীরা পর্যন্ত মাছ-মাংস খান এবং নিমন্ত্রিত শ্রমণও উভয় বস্তু প্ৰত্যাখ্যান করেন না। জৈনদের প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই ও হিস্তিনাং তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরম’ উপদেশটি অবাঙালিই দিয়েছেন। রাজপুতরা মাছ-মাংস খান, তাই বোধ করি মীরাবাঈ গেয়েছেন–
ফলমূল খেয়ে হরি যদি মেলে
তবে হরি হরিণের।
কাজেই মাছ-মাংস খাওয়ার জন্যে যদি বাঙালি অন্যান্য প্রদেশের বিরাগভাজন হয় তাতে শোক করবার কিছুই নেই। তার অর্থ শুধু এই যে, বাঙালি ভারতব্যাপী জৈন্য প্রভাবের ফলে সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি।
আমাদের দুই নম্বরের দোষ আমরা পরীক্ষা, আত্মা ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত কায়দায় পরীক্ষা আত্মা উচ্চারণ করি না। সংস্কৃত ভাষা পড়বার সময় এ সব শব্দ কি ভাবে উচ্চারণ করতে হবে সে আলোচনা পরে হবে, উপস্থিত দ্রষ্টব্য আমরা কেন বাঙলায় এ সব শব্দ বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করি।
এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয়, হিন্দি-গুজরাতী-মারাঠীরাও করেন। সাধারণ হিন্দি বলার সময় সবাই ক্ষত্রিয়কে শত্রিয় বলেন, লক্ষ্মণঝোলাকে লছমনঝোলাই বলে থাকেন। অর্থাৎ যে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে বাঙলা দেশ থেকে সংস্কৃত উচ্চারণ লোপ পায়, সেই ধ্বনি পরিবর্তন অন্যান্য প্রদেশেও ঘটেছিল—যার ফলে লক্ষ্মী লছমন হয়ে যান। পরবর্তী যুগে দেশজ হিন্দি, বাঙলা, গুজরাতীর উপর যখন সংস্কৃত তার আধিপত্য চালাতে গোল তখন আর সব প্রদেশ সে আধিপত্য মেনে নিল, কিন্তু বাঙলা স্বীকার করল না। বাঙালি তখন সেই ধ্বনি পরিবর্তনের আইন মেনে নিয়ে সংস্কৃত শব্দও বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করতে লাগল। এস্থলে বাঙালি পৃথিবীর আর সব জাত যা করেছে তাই করল—ইংরেজ, ফরাসি অথবা জর্মন যখন তার ভাষাতে গ্ৰীক বা লাতিন শব্দ উচ্চারণ করে তখন সেগুলো আপন আপন ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন দিয়েই করে, এমন কি গোটা বাক্যও আপনি কায়দায় উচ্চারণ করে (ইংরেজ এবং ভারতীয় আইনজ্ঞেরা nisi শব্দকে লাতিন নিসি উচ্চারণ না করে নাইসাই করেন, a priori কে আ প্রিয়োরি না বলে এ প্রয়োরাই বলেন)। হিন্দি গুজরাতী মারাঠী ইত্যাদি ভাষা সাধারণ শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন মেনে নিয়েছে (এমন কি মারাঠীরা জ্ঞানেশ্বরকে দানেশ্বর বলেন!), কিন্তু অপেক্ষাকৃত অচলিত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে।
অর্থাৎ আমরা consistent এবং অন্যান্য প্রদেশ এ নীতিটা মানেন না।
অবাঙালিরা তাই ভাবেন আমরা সংস্কৃত উচ্চারণ ‘বিকৃত’ করে তার উপর ‘অত্যাচার’ করেছি।
কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, বাংলা খুব তাড়াতাড়ি স্বাধীন হতে পেরেছে। আজ যে বাঙলা সাহিত্য হিন্দি, মারাঠী বা গুজরাতীকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পেরেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আমরা যদি আজও বিদ্যাসাগরী বাঙলা লিখতুম তাহলে ‘মেজদিদি’, ‘বিন্দু’, ‘জ্যাঠাইমা’ চরিত্র আঁকা অসম্ভবপর হত কি-না? ইংরেজের অত্যাচার-জর্জিরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ‘এই ভূতের খাজনা দেবো কিসে?’ উত্তরে বললেন, ‘শ্মশান থেকে মশান থেকে, ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।’ এ উত্তর কি বিদ্যাসাগরী বাঙলায় কখনো রূপ পেত?
ভাষা এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে আমাদের স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা দম্ভপ্রসূত নয়, সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞানজনিত নয়। ধর্ম জানেন, ভট্টপল্পী, নবদ্বীপ তথা বাঙলা দেশে সংস্কৃত চর্চা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়, কিন্তু বাঙলা বাঙলা এবং সংস্কৃত সংস্কৃত। বাঙলা ভাষা যখন আপনি নিজস্বতা খুঁজছিল তখন সে জানত না যে ইংরিজি, ফরাসি জর্মন একদা লাতিনের দাস্যবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভ করেই যশস্বিনী হয়েছে। বাঙলার এই প্রচেষ্টা ভগবানের দান এবং এই প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ জন্মেছিলেন বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ।
ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এখনও বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নি। প্রার্থনা করি, তারা যেন মহত্তর রবীন্দ্রনাথ, বিরাটতম। বঙ্কিম পান; কিন্তু ততদিন যদি আমরা এদের নিয়ে গর্ব না করি। তবে আমাদের নিমক-হারামির অস্ত থাকবে না।
***
অবাঙালিরা যখন বাঙালির প্রতি বিরক্ত হন তখন তাদের মুখে অনেক সময়ই শুনতে পাওয়া যায়, তোমরা বাঙালিরা আর কিছু পারো না পারো একটা জিনিসে তোমরা যে ওস্তাদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তোমাদের কেউ যদি সামান্য একটুখানি কিছু করতে পারে, তবে তাই নিয়ে তোমরা এত লাফালাফি মাতামাতি, সোজা ইংরিজিতে তাকে এত ‘বুসট’ করো যে অবাঙালি পর্যন্ত সেই প্রোপাগাণ্ডার ঠ্যালায় শেষটায় মেনে নেয় যে, যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে সে লোকটা সত্যি জব্বর কিছু একটা করেছে বটে। এই যেমন তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।
বাঙালি মাত্রেই এরকম ধারা কথা শুনলে পঞ্চাশ গোনবার উপদেশটা যে নিতান্ত অর্বািচীনের ফতোয় সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে অবাঙালিকে বেশ দু কথা শুনিয়ে দেয় এবং আমিও স্বীকার করি যে শোনবার হক তার তখন আলবত আছে।
আমি শোনাই না, কারণ আমি জানি অবাঙালি বেচারী পড়েছে মাত্ৰ গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার এবং চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ। হয়তো আরও দু-একখানা পড়েছে কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যে, ইংরেজি যার মাতৃভাষা নয় তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন যে এগুলোর মধ্যে এমন কি কবিত্ব, এমন কি তত্ত্ব আছে, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি খেতাব দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করা যায়! ইয়েট্স সাহেব যখন গীতাঞ্জলিকে প্রশংসা করে সপ্তম স্বর্গে তোলেন তখন তার একটা অর্থ করা যায় :-রবীন্দ্রনাথের ইংরিজিতে হয়তো এমন কোনো অদ্ভুত গীতিরস লুকোনো আছে যার স্বাদ পেয়ে ইংরিজিভাষী ইয়েট্স প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কিন্তু আমার মত বাঙালি অতটা উচ্চাঙ্গ ইংরিজি জানে না এবং আর পাঁচজন অবাঙালি যদি আমারই মত হয় তাতে আমার রাগ করার কি আছে?
সাধারণ বাঙালি যখন অবাঙালির এই ‘নীচ’ আক্রমণে মার মার করে তেড়ে যায় তখন সে ধরে নিয়েছে যে অবাঙালি রবীন্দ্রনাথের উত্তম উত্তম কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েও নিছক টিটেমি করে বাঙালির নিন্দে করছে। কাজেই ঝগড়াটা শুরু হয়। ভুল-বোঝা নিয়ে। কিন্তু একবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেলে কাদামাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে পাথরও ছোঁড়া হয়, তখন মানুষ জানা অজানাতে অন্যায় কথাও বলে ফেলে। তর্কের ঝোকে তখন অবাঙালি আমাদের অন্যান্য মহাপুরুষও যে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জোরেই খ্যাতনামা হয়েছেন সে কথা বলতেও কসুর করেন না।
আমি বাঙালি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তাই কি করে বুক ঠুকে বলি বলুন যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শ্ৰীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষের বিজ্ঞাপন দেবার প্রয়োজন আমরা কখনো অনুভব করি নি। এঁরা বাঙালির ধর্মজগতের গুরুর আসন গ্রহণ করে বাঙালি জাতটাকে গড়ে তুলেছেন। এ সত্যটা জানি এবং হিন্দি, গুজরাতী, মারাঠী, উর্দু নিয়ে চর্চা করছি বলে এ তথ্যটাও জানি যে ভগবান বোধ হয় বাঙালিকে নিতান্ত নিষ্কৰ্মা জেনেই দয়া করে একমাত্র তাকেই অকৃপণ হস্তে এতগুলি ধর্মগুরু দিয়ে ফেলার পর হাঁশিয়ার হয়ে অন্য প্রদেশগুলোর উপর কঞ্জুসি চালিয়েছেন।
আজকাল অবশ্যি ধর্ম রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে কি বাঙলা, কি বোম্বাই, কি দিল্লি সর্বত্রই পেনশন টানছেন। কিন্তু শ্ৰীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য বিবেকানন্দ এবং দূর শিষ্য সুভাষচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালির জাতীয়তাবোধ কতখানি জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন, সে কথা আমরাই এখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারি নি-বিজ্ঞাপন দেবে কে, বুসট্ আপ করবার গরজ কার? হা ধর্ম।
রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন আমাদের অচলায়তনের অন্ধ প্রাচীরে অনেকগুলো জানলা তৈরি করে দিয়েছেন—তার ভিতর দিয়ে আমরা পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান পেলুম। শ্ৰীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জনগণের সঙ্গে সে ঐতিহ্যের যোগসূত্র সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেলেন। তাই এক দিক দিয়ে আমরা যেমন বাইরের জিনিস নিতে শিখলুম, অন্য দিক দিয়ে ঠিক তেমনি আপন জিনিসকে অবহেলা না করে আপনি সংস্কৃতি সভ্যতা গড়ে তুললুম।
সব চেয়ে স্বপ্রকাশ হয়েছে এই তত্ত্বটি আমাদের সাহিত্যে। মাইকেল খ্রিস্টান, নজরুল মুসলমান এবং প্রমথ চৌধুরীকে ফরাসি বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হয় না। অথচ তিনজনই বাঙালি এবং তাঁরা যে সাহিত্য গড়ে তুলেছেন সেটি বাংলা সাহিত্য। কিন্তু এঁরাই শুধু নন, আর যে পাঁচজন বাঙালি সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তাদের সকলেই জানা-অজানাতে আমাদের ধর্মগুরুদের উপদেশ সাহিত্যক্ষেত্রে মেনে নিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের দরদী ঘরোয়া সাহিত্যের পশ্চাতে রয়েছে শ্ৰীরামকৃষ্ণের সরলতা, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পিছনে রয়েছে রামমোহনের বিদগ্ধ মনোবৃত্তি।
বহু আকস্মিক ঘটনা, বহু যোগাযোগের ফলে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ইংরেজি তথা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্যকলার চর্চা প্রধানত হয়েছিল কলকাতা এবং মাদ্রাজে। কিন্তু তামিল-ভাষাভাষীদের মধ্যে যাঁরা এসব দিকে আকৃষ্ট হলেন তারা মাতৃভাষার সেবা করলেন না। ফলে তারা বাঙালির চেয়ে ভালো ইংরিজি শিখলেন বটে-যদিও সে ইংরিজি সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত হল না-কিন্তু তামিল ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারল না। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের লোকমান্য টিলক (কথাটা তিলক নয়) এবং স্বামী দয়ানন্দ জন্মালেন বটে। কিন্তু সে সব প্রদেশে ইউরোপীয় সাহিত্য প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রসারণ হল না বলে মারাঠী, গুজরাতী সাহিত্য আজও বাঙলার অনেক পিছনে।
অবজ্ঞাপ্রসূত প্রাদেশিক বিদ্বেষ তাহলে ঘুচিবে কবে? যেদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অন্য প্রদেশের ভাষা শেখাবার ব্যাপক ব্যবস্থা হবে সেদিন থেকে। ইংরেজ এ ব্যবস্থা করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করে নি।–তার কারণটাও অনায়াসে বোঝা যায়-কিন্তু আমাদের বেশ ভালো করে মেনে নেওয়া উচিত, সর্বপ্রদেশের সর্বপ্ৰচেষ্টার সঙ্গে যদি আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী বহু প্ৰাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সংযুক্ত না হয়, তবে অবজ্ঞাপ্রসূত এ সব বিদ্বেষ কস্মিনকালেও যাবে না, এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা শিখলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না।
প্রত্যেক ছাত্রই যে বারোটা প্ৰাদেশিক ভাষা শিখবে এ প্রস্তাব কেউ করবে না, মানবেও না। ব্যবস্থাটা হবে এই যে বহু ছাত্র মারাঠী, বহু ছাত্র গুজরাতী, অন্যেরা তালিম অথবা কানাড়া অথবা অন্য কোনো প্ৰাদেশিক ভাষা শিখবে, তারা ঐসব ভাষা থেকে উত্তম উত্তম পুস্তক বাঙলায় অনুবাদ করবে, ঠিক সেইরকম বাঙলা বইও নানা ভাষায় অনুদিত হবে। ফলে এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের সাহিত্য চিনতে শিখবে এবং তারপরেও যদি বিদ্বেষ থেকে যায়। তবে তার জন্য অন্তত আমাদের শিক্ষা-প্ৰদ্ধতিকে দোষ দেওয়া যাবে না।
গাইড
দিল্লিতে একটি সরকারি টুরিস্ট বুরো বসেছে। তার প্রধান কর্ম টুরিস্টদের সদুপদেশ দেওয়া, এটা সেটা করে দেওয়া এবং বিচক্ষণ গাইডের তদারকিতে শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখানে।
এই সম্পর্কে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, দিল্লিতে বিচক্ষণ গাইডের বিলক্ষণ অভাব। আমি পত্ৰলেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।
‘পাণ্ডা’ এবং ‘গাইড’ হিরোদেরে একই মাল। তীর্থস্থলের গাইডকে পাণ্ডা বলা হয়–তাই গয়াতে আপনি পাণ্ডা ধরেন, কিংবা বলুন পাণ্ডা আপনাকে ধরে—আর ঐতিহ্যসিক ভূমি এবং তীর্থক্ষেত্রের যদি সমন্বয় ঘটে। তবে সেখানে পাণ্ডা এবং গাইডের সমন্বয় হয়। যেমন জেরুজালেম। তিন মহা ধর্ম-ক্রীশ্চান, ইহুদী এবং মুসলমান—এখানে এসে সম্মিলিত হয়েছে। তার উপর জেরুজালেমের অভেজাল ঐতিহ্যসিক মূল্যও আছে। ফলে পৃথিবীর হেন দেশ হেন জাত নেই যেখান থেকে তীর্থযাত্রী (পাণ্ডার বলির পাঠা) এবং টুরিস্ট (গাইডের কুরবানীর বকরি) জেরুজালেমে না আসে।
দিল্লি অনেকটা জেরুজালেমের মত। এর ঐতিহ্যসিক মূল্য তো আছেই, তীর্থের দিক দিয়ে এ জায়গা কম নয়। চিশতী সম্প্রদায়ের যে পাঁচ গুরু এদেশে মোক্ষলাভ করেছেন তাদের তিনজনের কবর দিল্লিতে। কুতুব-মিনারের কাছে কুৎব উদদীন বখতিয়ার কাকীর (ইনি ইলতুৎমিশ-অলতমশের গুরু) কবর, হুমায়ুনের কবরের কাছে নিজামউদদীন আওলিয়ার কবর (ইনি বাদশা আলাউদদীন খিলজী এবং মুহম্মদ তুঘলুকের গুরু) আর দিল্লির বাইরে শেষ গুরু নাসিরউদ্দীন চিরাগ-দিল্লির কবর। আর কলকাজী, যোগমায়া তো আছেনই।
এসব জায়গায় পাণ্ডারা যা গাঁজাগুল ছাড়ে সে একেবারেই অবর্ণনীয়। এদিকে বলবে যেটা হচ্ছে আকবরের দু-ভাইয়ের কবর, ওদিকে বলবে, তিন হাজার বছরের পুরনো এই কবরের উপরকার এমারত!
বেঙ্গল কেমিকেলের আমার এক সুহৃদ গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। পাণ্ডা দেখালে এক দোলন-ভক্তিভরে বললে, এ দোলায় দোল খেতেন। রাধাকৃষ্ণ পাশাপাশি বসে। বন্ধুটি নাস্তিক নন, সন্দেহাপিশাচ। বললেন, ‘যে কড়ির সঙ্গে দোলনা ঝোলানো রয়েছে, তাতে তো লেখা রয়েছে, টাটা কোম্পানির নাম; আমি তো জানতুম না, টাটা এত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান!’
পরদিন বৃন্দাবন থেকে সজল নয়নে বিদায় নেবার বেলা বন্ধু সে জায়গায় গিয়ে দেখেন, কড়িতে প্ৰাণপণ পলস্তারার পর পালস্তারা রঙ লাগানো হচ্ছে।
***
দিল্লিতে ভালো গাইডের সত্যই অভাব। সখা এবং শিষ্য শ্ৰীমান বিবেক ভট্টাচার্য কপালী লোক। তিনি কখনো কখনো ভালো গাইড পেয়ে যান-সে বিষয়ে তিনি ‘দেশে’ মনোরম প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু সচরাচর আপনার কপালে এখানে যা গাইড জুটবে তার না জানে ইতিহাস এবং না পারে ছড়াতে গাঁজাগুল।
ভালো গাইড মানে কথকঠাকুর, আর্টিস্ট। তাঁর কর্ম হচ্ছে, ইতিহাস আর কিম্বদন্তী মিলিয়ে মিশিয়ে আপনাকে গল্পের পর গল্প বলে যাওয়া, আর সে সব গল্প শুনে আপনি এত খুশি যে দিনের শেষে তাকে পাঁচ টাকা দিতে আপনার বুক কচকচ করে না।
একদা ভিয়েনা শহরে আমি এই রকম একটি গাইড পেয়েছিলুম। শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাতে দেখাতে বললে, ‘এই দেখুন শ্যোনক্রন প্রাসাদ। রাজাধিরাজ ফ্রানৎসয়োসেফ এখানে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতেন পলটনের কুচকাওয়াজ। দেশ-বিদেশের গেরেমভারী রাজকর্মচারি রাজদূতেরা হুজুরের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে দেখতেন আমাদের শৌর্য বীর্য আমাদের ঐশ্বর্য। তারপর হুজুর বেরতেন সোনার-পাত মোড়া গাড়িতে, বিবিসিাহেবা বেরতেন রূপের গাড়িতে। আহা, কোথায় গেল সে সব দিন!’
খানিকক্ষণ পর বাড়ি ফেরার পথে গাইড বলল, ‘দেখুন দেখুন, এই ছোট্ট বাড়িখানা, ফ্রানৎসয়োসেফ যে রকম রাজার রাজা ছিলেন, ঠিক তেমনি সঙ্গীতে রাজার রাজা বেটোফেন দৈন্যে-ক্লেশে কাতর হয়ে এই লঝঝড় বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার শেষ কটি সিমফনি-সেই ত্ৰিলোকবিখ্যাত স্বর্গীয় সঙ্গীতসুধা কে না পান করেছে বলুনতিনি এইখানেই রচেছিলেন।’
আমি করজোড়ে সে বাড়িকে নমস্কার করলুম। দেখে গাইডের হৃদয়ে বিষাদে হরিষ দেখা দিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে, ‘একটুখানি চক্কর মেরে বেটোফেন যে বাড়িতে দেহত্যাগ করেছিলেন সেইটো দেখিয়ে দাও।’
সে বাড়ির সামনে আমরা দুজনাই নিস্তব্ধ। এই জীৰ্ণ শীর্ণ দরিদ্র গৃহে রাজাধিরাজ বেটোফেন দেহত্যাগ করলেন!
আমরা বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ গাইড ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেন, ‘একটু তাড়াতাড়ি চালাও বাছ, ঐ পাশের বাড়িতে আমার শাশুড়ি থাকেন, খাণ্ডার রমণী, পাছে না দেখে ফেলে।’
গীতা-রহস্য
গীতার মত ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। তার প্রধান কারণ, গীতা সর্বযুগের সর্ব মানুষকে সব সময়েই কিছু না কিছু দিতে পারে। অধ্যাত্মলোকে চরম সম্পদ পেতে হলে গীতাই অত্যুত্তম পথপ্রদর্শক, আর ঠিক তেমনি ইহলোকের পরম সম্পদ পেতে হলে গীতা যেরকম প্রয়োজনীয় চরিত্র গড়ে দিতে পারে, অন্য কম গ্রন্থেরই সে শক্তি আছে। ঘোর নাস্তিকও গীতাপাঠে উপকৃত হয়। অতি সবিনয়ে নিবেদন করছি, এ কথাগুলো আমি গতানুগতিকভাবে বলছি নে, দেশ-বিদেশে গীতাভক্তদের সাথে একসঙ্গে বসবাস করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছে।
তাই গীতার টীকা রচনা করা কঠিনও বটে, সহজও বটে। সর্বধর্ম সর্বমার্গের সমন্বয় যে গ্রন্থে আছে তার টীকা লেখার মত জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অল্প লোকেরই থাকার কথা; আর ঠিক তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু না কিছু সমর্থন গীতাতে পায় তখন তার পক্ষে একমাত্ৰ গীতার টীকা লেখাই সম্ভবপর হয়-একমাত্র গীতাই তখন সে-ব্যক্তির সামান্য অভিজ্ঞতা বিশ্বজনের সম্মুখে রাখবার মত সাহসে প্রলোভিত। করতে পারে।
লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের ‘গীতারহস্য’ প্রথম শ্রেণীর টীক। ‘গীতা রহস্যে’ লোকমান্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অভিমতও আছে বটে, কিন্তু এ গ্রন্থের প্রধান গুণ, তার তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী। এই তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং এই শতকের প্রথম দিকেই সর্বপ্রথম সম্ভবপর হয়,—কারণ তার পূর্বে সর্বধর্মে জ্ঞান আহরণ করতে হলে সর্বভাষা আয়ত্ত করতে হত, এবং সে কর্ম অসাধারণ পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব। ঊনবিংশ শতকে নানা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হল এবং বিংশ শতকে সমস্ত উপাদান এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর সুসজ্জিত হয়ে গেল যে, তখনই প্রথম সম্ভবপর হল তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গীতা বিচার করা।
এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশে-বিদেশে বহুতর সাধক, গুণীজ্ঞানী গীতাকে কেন্দ্র করে নানা ধর্মালোচনা করেছেন। বাংলা ইংরেজি এই দুই ভাষাতেই গীতা সম্বন্ধে এত পুস্তক জমে উঠেছে যে, তাই পড়ে শেষ করা যায় না। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা, ফরাসী এবং বিশেষ করে জর্মনে গীতা সম্বন্ধে আমরা বহু উত্তম গ্রন্থ দেখেছি।
তৎসত্ত্বেও বলতে বাধ্য, লোকমান্যের গ্ৰন্থখানি অনন্যসাধারণ। এ পুস্তক লোকমান্য মান্ডালে জেলে বসে মারাঠী ভাষায় লেখেন।
‘অনুবাদ সাহিত্য’ প্ৰবন্ধ লেখার সময় আমি এই পুস্তকখানার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলুম। স্বৰ্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পুস্তকখানির অনবদ্য অনুবাদ বাংলা ভাষায় করে দিয়ে গিয়ে গৌড়জনের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়ে গিয়েছে। এ অনুবাদের সঙ্গে করুণ রসও মিশ্রিত আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি,–
‘লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক তঁহার প্রণীত ‘গীতা-রহস্য’ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি আপণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাহার অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ কামনায় বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে,-অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্ৰহণ করিয়াছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায়, এতদিন পরে উহা গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করিয়া আমার এই কঠিন ব্ৰত উপন্যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।’–
তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যা বলেছেন, পাঠকের দৃষ্টি আমি সেদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চাই। :-
‘কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল—এই অনুবাদ গ্ৰন্থখানি মহাত্মা টিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।’
যতবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদখানা হাতে নিই, ততবারই আমার মন গভীর বিস্ময়ে ভরে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদ ৮৭২ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। এই অনুবাদ কর্ম প্রায় ষাট বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্ৰনাথ আরম্ভ করেন। যৌবনে তিনি বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন মহারাষ্ট্রে ছিলেন তখন মারাঠী শিখেছিলেন এবং ততদিনে নিশ্চয়ই সে ভাষার অনেকখানি ভুলে গিয়েছিলেন-রাচীতে বসবাস করে দূর মারাঠা দেশের সঙ্গে সাহিত্যিক কেন, কোনো প্রকারের যোগ রাখাই কঠিন। তাই ধরে নিচ্ছি, সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি নূতন করে মারাঠী শিখে প্ৰায় তিন লক্ষ মারাঠী শব্দ বাংলায় অনুবাদ করেছেন, মাসের পর মাস তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তার প্রকাশের তত্ত্বাবধান করেছেন, এবং সর্বশেষে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন,-
‘গ্রন্থের প্রাফ সংশোধনে আদি-ব্ৰাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্ৰীযুক্ত সুরেশচন্দ্ৰ সাংখ্যবেদান্ততীৰ্থ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।’
অর্থাৎ প্রুফ দেখার ভারও আসলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপরেই ছিল।
তাই বিস্ময় মানি যে, এই হিমালয় উত্তোলন করার পর যখন জ্যোতিরিন্দ্ৰনাথ লিখলেন লোকমান্য ইহলোকে নেই তখন তিনি সেই শোক প্রকাশ করলেন, ‘কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল’ বলে। এ শোক, এ আক্ষেপ প্রকাশ করার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাণ্ডারে কি ভাষা, বর্ণনশৈলী, ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য ছিল না? মৃচ্ছকটিকা, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, নীলপাখি অনুবাদ করার পরও কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে করুণ রস প্রকাশ করার ক্ষমতা অলব্ধ ছিল?
তাই মনে হয়, যিনি বহু রসের সাধনা আজীবন করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে সর্বরিস মিলে গিয়ে তাঁর মনে এক অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যের অভূতপূর্ব শান্তি এনে দেয়। অথবা কি দীর্ঘ দিনযামিনী গীতার আসঙ্গ লাভ করে জ্যোতিরিন্দ্ৰনাথ সেই বৈরাগ্যবিজয়ী কর্মযোগে দীক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেখানে মানুষ কর্ম করে অনাসক্ত হয়ে কেবলমাত্র বিশ্বজনের উপকারার্থে? তাই মনে হয়, সাধনার উচ্চমত স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও জ্যোতিরিন্দ্ৰনাথের স্পর্শকাতরতা লোপ পায় নি-লোকমান্যকে সম্পূর্ণ পুস্তক স্বহস্তে নিবেদন করতে পারেন। নি বলে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে বেদনা প্রকাশ করেছেন শোকে আতুর না হয়ে, গভীর্য এবং শাস্তরসে সমাহত হয়ে।
কিন্তু এ সব কথা বলা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। আমার ইচ্ছা বাঙালি যেন এ অনুবাদখানা পড়ে, কারণ লোকমান্য রচিত ‘গীতা-রহস্যে’র ইংরেজি অনুবাদখানা অতি নিকৃষ্ট। যেমন তার ভাষা খারাপ, তেমনি মূলের কিছুমাত্র সৌন্দর্য কণামাত্র গান্তীর্য সে অনুবাদে স্থান পায় নি। অথচ বাংলা অনুবাদে, আবার জোর দিয়ে বলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদে, মূলের কিছুমাত্র সম্পদ নষ্ট হয় নি, মূল মারাঠী পড়ে মহারাষ্ট্রবাসী যে বিস্ময়ে অভিভূত হয়, অনুবাদ পড়ে বাঙালিও সেই রসে নিমজ্জিত হয়।
কিন্তু অতিশয় শোকের কথা-এ অনুবাদ গত আট বৎসর ধরে বাজারে আর পাওয়া যায় না। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার পর এ পুস্তকের আর পুনমুদ্রণ হয় নি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা কোনো উদ্যোগী বাঙালি প্রকাশক যেন পুনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে এ পুস্তক পুনরায় প্রকাশ করেন।
আমার কাছে যে অনুবাদখানি রয়েছে তাতে লেখা আছে :–
All rights reserved by
Messrs, R. B. Tilak and S. B. Tilak,
568 Narayan Peth, Poona City. *
—-
* সম্প্রতি খবর এসেছে, বিশ্বভারতীতে পুস্তকখানি পাওয়া যাচ্ছে।
গুরুদেব
রবীন্দ্রনাথের শিষ্যদের ভিতর সাহিত্যিক হিসাবে সর্বোচ্চ আসন পান শ্ৰীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। তিনি যে রকম রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি, তেমনি বিধিদাত্ত রসবোধ তার আগের থেকেই ছিল। ফলে তিনি সরস, হালকা কলমে রবীন্দ্ৰনাথের দৈনন্দিন জীবন, খুশ-গল্প, আড্ডা-মজলিস সম্বন্ধে যা লিখেছেন তারপর আর আমার কিছু লিখবার মত থাকতে পারে না। কারণ বিশীদা যে মজলিসে সবচেয়ে উচু আসন পেয়েছেন সে মজলিসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে। যদি নিতান্তই আমাকে কোনো স্তোকাসন দেওয়া হয় তবে সেটা হবে সর্বনিম্নে।
কিন্তু বহু শাস্ত্রে বিধান আছে সর্বজ্যেষ্ঠ যদি কোনো কারণে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিতে পারে, তবে দেবে সর্বকনিষ্ঠ। এই ছেলেধরার বাজারে কিছু বলা যায় না-গুরুদেবকে স্মরণ করার সময় আমরা সবাই একবয়সী ছেলেমানুষ, রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আজকের শিশুবিভাগের কনিষ্ঠতম আশ্রমিক-কাজেই বিশীদার যদি ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তবে আমার আকন্দাঞ্জলির প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে মা ‘বসুমতীর’ কাছে এটি গচ্ছিত রাখছি।
ব্যাপকর্থে রবীন্দ্রনাথ তাবৎ বাঙালির গুরু, কিন্তু তিনি আমাদের গুরু শব্দার্থে। এবং সে গুরুর মহিমা দেখে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়েছি। ব্যক্তিগত কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকে কিন্তু এ স্থলে ছাত্রের কর্তব্য সমাধান করার জন্য বলি, শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর বার্লিন, প্যারিস, লন্ডন, কাইরো বহু জায়গায় বহু গুরুকে আমি বিদ্যাদান করতে দেখেছি কিন্তু এ গুরুর অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না। কত বৎসর হয়ে গেল, কিন্তু আজও মনের পটের উপর রবীন্দ্রনাথের আঁকা কীটসের আটামের ছবি তো মুছে গোল না। কীটস হেমস্তের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে যে আরও বেশি উজ্জ্বল করা যায়, এ কথা তো কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না। ইংরাজিতে প্ৰবাদ আছে, ‘You do not paint a lily’—তাই মনে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্রনাথ কীটসের হেমন্ত-লিলিকে মধুরতর প্রিয়তর করতেন কোন জাদুমন্ত্রের জোরে?
তুলনা না দিয়ে কথাটা বোঝাবার উপায় নেই। ইংরেজি কবিতা পড়ার সময় আমাদের সব সময় মনে হয়, ইংরিজি কবিতা যেন রূপকথার ঘুমন্ত সুন্দরী। তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছসিত প্রশংসা করি, কিন্তু তার বাক্য-হাস্য-নৃত্য রস থেকে বঞ্চিত থাকি বলে অভাবটি এতই মৰ্মদ্ভদ হয় যে, শ্যামলী স্কুলাঙ্গী জাগ্ৰতা গীেড়াজার সঙ্গসুখ তখন অধিকতর কাম্য বলে মনে হয়।
রবীন্দ্রনাথের বর্ণনশৈলী ভানুমতী মন্ত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি তাঁর সোনার কাঠির পরশ দিয়ে কীটসের হৈমন্তীকে জাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের বিদ্যালয়ের নিভৃত কোণে। গুরুদেব কীটসের এক ছত্র কবিতা পড়েন, নিদ্রিতা সুন্দরীকে চোখের সামনে দেখতে পাই। তিনি তার ভাষার সোনার কাঠি ছোয়ান, সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী নয়ন মেলে তাকায়। গুরুদেবের কণ্ঠে প্ৰাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, সুন্দরী নৃত্য আরম্ভ করে। গুরুদেব তাঁর বীণার তারে করাঙ্গুলিস্পর্শে ঝঙ্কার তোলেন, সুন্দরী গান গেয়ে ওঠে।
কীটস, শেলি, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডসওয়ার্থকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এ ইন্দ্ৰজাল কতবার দেখেছি আর ভেবেছি, হায়, এ বর্ণনা যদি কেউ লিখে রাখত তাহলে বাঙালি তো তার রস পেতই, বিলেতের লোকও একদিন ওগুলো অনুবাদ করিয়ে নিয়ে তাদের নিজের কবির কত অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য দেখতে পেত। কিন্তু জানি ভানুমতীর ছবি ফটোগ্রাফে ওঠে না, গুরুদেবের এ বর্ণনা করো কলম কালিতে ধরা দেয় না। যেটুকু দিয়েছে সেটুকু আছে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের ভাণ্ডারে।
তারপর একদিন বেলজিয়মে থাকার সময় বিলেত যাবার দরকার হল। ইচ্ছে করেই যাওয়াটা পিছিয়ে দিলুম— তখন বসন্ত ঋতু। কীটসের ‘হৈমন্তী’র সঙ্গে দেখা হতে অনেক বাকি। সায়েব-মেমসায়েবরা অসময়ে দেখা করেন না।
বিলিতী হৈমন্তীকে দেখে মুগ্ধ হলুম, অস্বীকার করব না। কীটসের ফিরিস্তি মিলিয়ে নিখাঁশির বর্ণনা টায় টায় মিলে গেল, কিন্তু গুরুদেবের হৈমন্তীর সন্ধান পেলুন না। কীটসের সুন্দরীকে বার বার তাকিয়ে দেখি আর মনে হয়, আগের দিনের বেলাভূমিতে কুড়িয়ে-পাওয়া ঝিনুক ঘরের ভিতরে এসে স্নান হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের সূর্যাস্তের সময় যে লীলাম্বুজ নীলাম্বরের সৃষ্টি করেছিল, যার মাঝখানে এই শক্তিই ইন্দ্ৰধনু বৰ্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করেছিল, গৃহকোণের দৈনন্দিনতার মাঝখানে সে যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, ‘তুলসীর মূলে’ যে ‘সুবৰ্ণ দেউটি’ দশদিক উজ্জ্বল করেছিল। সেই দেউটি দেবপদস্পর্শলাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে স্নানমুখে আপন দৈন্য প্রকাশ করতে লাগল।
তারপর আরও কয়েক বৎসর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শ্ৰীযুক্ত অমিয় চক্রবতীর কাছ থেকে তার পেলুম, জর্মনির মারবুর্গ শহরে গুরুদেব আমাকে ডেকেছেন— জানতেন আমি কাছাকাছি আছি।
মারবুর্গের সে জনসভার বর্ণনা আমি অন্যত্র দিয়েছি। আজ শুধু বলি, গুরুদেব সেদিন যখন ‘ঘন ঘন সাপ খেলাবার বাঁশী’ বাজালেন তখন মারবুর্গের পরবে জমায়েত তাবৎ জার্মানির গুণী-জ্ঞানী মানী তত্ত্ববিদের সেরারা’ মন্ত্রমুগ্ধ সৰ্পের মত অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘ এক ঘণ্টাকাল গুরুদেব বক্তৃতা দিলেন,- একটি বারের মত সামান্যতম একটি শব্দও সেই সম্মিলিত যোগসমাধির ধ্যান-ভঙ্গ করল না। আমার মনে হল গুরুদেব যেন কোন এক অজানা মন্ত্রবলে সভাস্থ নরনারীর শ্বাস-প্ৰশ্বাস পর্যন্ত স্তম্ভন করে দিয়েছেন— ডাইনে বাঁয়ে তার শব্দটুকুও শুনতে পাই নি।
আমার মনে হয়েছিল, সভাগৃহ থেকে বেরুতে গিয়ে দেখব। সেই বিপুলকলেবর অট্টালিকা বাল্মীকিন্তুপে নিরুদ্ধ নীরন্ধ হয়ে গিয়েছে।
সেই জনতার মাঝখানেই গুরুদেবকে প্ৰণাম করলুম- জানি নে তো কখন আবার দেখা হবে। এত সব গুণী-জ্ঞানীর মাঝখানে আমার জন্য কি আর বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হবে? কিন্তু ভুলে গিয়েছিলুম গুরুদেবেরই কবিতা :–
আমার গুরুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মানিক জ্বলে?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটি ঢেলারে।
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে কজন আছে
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন
তাই আমি তাঁর চেলারে।
বিশাল জনতার উদ্বেলিত প্ৰশংসা-প্ৰশস্তি পাওয়ার পরও, আমি যখন প্ৰণাম করে দাঁড়ালুম, তিনি মৃদুকণ্ঠে শুধালেন, ‘কি রকম হল?’
আমি কোনো উত্তর দিই নি।
শহরের উজির-নাজীর-কেটালরা গুরুদেবকে তার হোটেলে পৌঁছে দিলেন। আমি পরে সেখানে গিয়ে শ্ৰীযুক্ত চক্রবতীর কাছ থেকেই বিদায় নিতে চাইলুম। তিনি বললেন, ‘সে কি কথা, দেখা করে যান।’
আমি দেখা হবে শুনে খুশি হয়ে বললুম, ‘তাহলে আপনি গিয়ে বলুন।’
শ্ৰীযুক্ত চক্রবর্তী বললেন, ‘সে তো আর পাঁচজনের জন্য। আপনি সোজা গিয়ে নক করুন।’
গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু হাসিমুখে বসতে বললেন। তারপর ভালো করে তাকিয়ে বললেন, ‘এত রোগ হয়ে গিয়েছিস কেন?’
আমি মাথা নীচু করে চুপ করে রইলুম।
কিছু কথাবার্তা হল। আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে। যখন উঠলুম। তখন বললেন, ‘অমিয়কে ডেকে দে তো।’
চক্রবর্তী বলেন। গুরুদেব বললেন, ‘অমিয়, একে ভালো করে খাইয়ে দাও।’
জানি পাঠকমণ্ডলী এই তামসিক পরিসমাপ্তিতে ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু সোক্রাতেসের চোখে যখন মরণের ছায়া ঘনিয়ে এল আর শিষ্যের কানের কাছে চিৎকার করে শুধালেন, ‘গুরুদেব, কোনো শেষ আদেশ আছে?’
তখন সোক্রাতেস বললেন, ‘হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পরশুদিন যে মুরগিটা খেয়েছিলুম তার দাম দেওয়া হয় নি। দিয়ে দিয়ো।’ এই সোক্রাতেসের শেষ কথা।
সব দিকে যাঁর দৃষ্টি তিনিই তো প্রকৃত গুরু এবং তাও মৃত্যুর বহু পূর্বে।
জিদ-ওয়াইল্ড্
আঁদ্রে জিদের বই এবং বিশেষ করে তার জুর্নালগুলো (ডায়েরি) বিশ্ববিখ্যাত। আর পাঁচজনের মতো আমিও সেগুলো পড়েছি, তাঁর পরলোকগমনের পর ফ্রান্স দেশে তাঁর সম্বন্ধে যেসব লেখা বেরিয়েছে তারও কিছু কিছু নেড়েচেড়ে দেখেছি, কিন্তু তবু মেনে নিতেই হল যে, ঠিক ঠিক হদিসটি পেলুম না-জিদকে ফেলি কোন পর্যায়ে, কপালে টিকিট সাঁটি কোন রঙের? অথচ গুরুর আদেশ জিদ সম্বন্ধে লিখতে হবে-উপায় কি?
একটা উপায় আছে, সেটি হচ্ছে জিদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলোচনা করা। এই ধরুন না, অস্কার ওয়াইলাড়ু। জিদ তাকে বিলক্ষণ চিনতেন এবং ওয়াইলড়ও তাকে স্নেহ করতেন। ওয়াইলড়। তখন খ্যাতনামা পুরুষ, প্যারিসে এলে তাঁর পিছনে ফেউ লেগে যেত; তার উপর ওয়াইলন্ডু বলতে পারতেন খাসা ফরাসী। জিদই তার চটি বই ‘অস্কার ওয়াইলডের স্মরণেতে লিখেছেন, ‘ওয়াইলডু অত্যুৎকৃষ্ট ফরাসী জানতেন তবু মাঝে মাঝে ভান করতেন যেন জুতসই শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না-অবশ্য তখন তাঁর মতলব হত। ঐ কথাগুলোর উপর বিশেষ করে জোর দেবার। উচ্চারণে তাঁর প্রায় কোনো ভুলই ছিল নাশুধু ইচ্ছে করে দুটো একটা শব্দ এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যাতে করে সেগুলো ভারি নূতন ধরনের চমক দিয়ে দিত। প্রথম যে সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সেদিন তিনি একটানা আমাদের গল্প শুনিয়েছিলেন। কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া, আর সে সন্ধ্যার গল্পগুলো তার সবচেয়ে ভালো গল্প বলেও ধরে নেওয়া যায় না। হয়তো ওয়াইলাড়ু আমাদের চিনতেন না বলে আমাদের গ্রহণ করার ক্ষমতা পরখ করে নিচ্ছিলেন। ঐ ছিল তাঁর স্বভাব-তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক-যে লোক যে জিনিসের রস বুঝতে পারবে না। তাকে চিনি সে জিনিস ককখনো পরিবেশন করতেন না। যার সে রকম রুচি তাকে ঠিক সেই রকমেরই মাল দিতেন। তিনি। যারা তার কাছ থেকে কোনো জিনিসের প্রত্যাশা করত না তারা পেতও না কিছু-কিংবা হয়ত পেত সামান্য একটুখানি গোঁজলা। আর সবচেয়ে তিনি পছন্দ করতেন। খুশগল্প বলে পাঁচজনকে খুশ করে রাখতে, তাই অনেকেই যাঁরা ভেবে নিয়েছেন যে, তাঁরা ওয়াইলাড়ুকে চিনতে পেরেছেন, তারা শুধু তাকে চিনেছেন খুশি দেনেওয়ালা হিসেবে (amuseur = amuser)।
জিদ এখানে একটুখানি ইঙ্গিত করেছেন যে, বেশির ভাগ লোকই ওয়াইলড়কে চিনেছে কেমন যেন একটু ‘ভাঁড়’ ‘ভাঁড়’ রূপে এবং সেইটিই তাঁর আসল রূপ ছিল না।
মনে হচ্ছে এর থেকে জিদ কিঞ্চিৎ শিখে নিয়েছিলেন। কারণ পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, ‘ঐ ছিল তার স্বভাব–তা সে বুদ্ধিমানের হোক, আর বোকারই হোক–সবাইকে আপন রুচি অনুযায়ী পরিবেশন করার।’ তাই বোধ করি; জিদ সেই প্রথম যৌবনেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে, ওটা বোকারই কর্ম, আর তিনি অন্য কারোর রুচির বিলকুল তোয়াক্কা না করে। টক-টক হক কথা বলে যাবেন।
সে না হয় বুঝলুম। অপরকে টক কথা শুনিয়ে দেওয়া খুব কঠিন কর্ম নয়—আমরা সবাই জানা-অজানাতে হরদম কয়ে থাকি-কিন্তু প্রশ্ন, নিজের সম্বন্ধে টক কথা পাঁচজনকে শুনিয়ে বলতে পারে কটা লোক? জিদ। পারতেন। কি না?
ওয়াইলডু কোন অপরাধে জেলে গিয়েছিলেন সে-কথা সকলেই জানেন। জেল থেকে বেরিয়ে ওয়াইলডু দেখেন লন্ডন-সমাজ তার তাবৎ দরজা দড়াম করে তাঁর মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তখন গেলেন ফ্রান্স। প্যারিসেও গোড়ার দিকে ঐ একই অবস্থা হতে পারে ভেবে তিনি গেলেন একটি ছোট নির্জন শহরে। খবর পেয়ে জিদ। তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে গিয়ে জখমী ওয়াইলডের বিস্তর তত্ত্বতাবাশ করলেন। জিন্দ তাঁর অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন উপযুক্ত চটি বইয়ে। পাঁচজনে কি বলবে না বলবে তার তোয়াক্কা জিদ। তখন করেন নি; সে কথাটা তিনি না বললেও স্পষ্ট বোঝা যায়।
তারপর ওয়াইলডু ফিরে এলেন প্যারিসে। জিদের সঙ্গে তাঁর দুচার বার দেখাসাক্ষাৎ হল। ক্রমে ক্ৰমে দেখা গেল, প্যারিসও যে শুধু ওয়াইলডের ইকো-নাপিতই বন্ধ করেছে তা নয়, তার বন্ধুবান্ধবের অনেকেও তাকে কুণ্ঠরোগীর মতো বর্জন করতে আরম্ভ করেছেন। জিদ লিখেছেন, ‘ওয়াইলন্ডু যখন দেখতে পেলেন দু-চারখানা দরজা তাঁর জন্য বন্ধ তখন তিনি আর কোনো দরজাতেই কড়া নাড়লেন না–ছন্নের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।
এমন সময় একদিন জিদ দেখতে পেলেন, ওয়াইলডু এক কাফের বারান্দায় বসে আছেন। স্বীকার করি, ও রকম জায়গায় হঠাৎ মোলাকত হয়ে যাওয়াতে আমি একটুখানি অস্বস্তি অনুভব করলুম-চতুর্দিকে ভিড়। বন্ধু ‘জি-’ ও আমার জন্য ওয়াইলন্ডু দুটো ককটেল অর্ডার দিলেন। আমি তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসতে যাচ্ছিলুম যাতে করে লোকজনের দিকে পিঠ ফিরানো থাকে। কিন্তু ওয়াইলাড়ু ভাবলেন, আমি পাশে বসতে বোকার মতো নিরর্থক লজ্জা পাচ্ছি (হায়, ওয়াইলডু সম্পূর্ণ ভুল করেন নি) তাই পাশের চৌকি দেখিয়ে বললেন, আঃ, আমার পাশে এসে বসে না; আমি আজকাল বড্ড একলা পড়ে গিয়েছি।’
তারপর দুজনাতে কি কথাবার্তা হল সে কথা আরেক দিন হবে। উপস্থিত লক্ষ্য করার বস্তু যে, জিদও জনমতের ঠেলায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন। এবং যে ব্যবহার করলেন তাকে সুব, ক্যাডের আচরণ বলা যেতে পারে। বাঙলা কথায় একদম ছোটলোকোমি করলেন।
একদিন জিদ নিৰ্ভয়ে যেচে গিয়ে ওয়াইলডের সঙ্গে দেখা করেছিলেন লোকনিন্দার পরোয়া না করে, এবং আশ্চর্য তাই নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র গর্ব করেন নি এবং আরো যখন অন্যায় আচরণ করলেন তখনও সেটা লুকোলেন না। শুধু তাই নয়, পাঠক যাতে অতি নির্মমভাবেই তাঁর মাথায় ঘোল ঢালতে পারে তাই কোনো প্রকারের অজুহাত বা আত্মনিন্দাও পেশ করলেন না।
কি উপন্যাস, কি ছোট গল্প, কি জুর্নাল, সর্বত্রই জিদ। এই আশ্চর্য সাধুতা দেখিয়েছেন।*
——-
* Andre Gide : Oscar Wilde. In memoriam, Paris, Mercure de France.
জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা
ম্যাট্রিক পাশের লিস্টে নাম দেখে। যেমন ইয়া আল্লা’ বলে ছেলে-ছোকরার লম্ফ দিয়ে ওঠে আমাদের অখণ্ড স্বরাজলাভের আনন্দোল্লাস তার সঙ্গে তুলনীয়। এমন কি, ম্যাট্রিকেও যদি পাঠকের মন সন্তুষ্ট না হয় তাহলে বি.এ. এম.এ. পি.এইচ. ডি. ডি. লিট যা খুশি বলতে পারেন তাতেও কোনো আপত্তি নেই। শুধু তাই নয়-এ স্বাধীনতা পাশের আনন্দ অন্য সব পাশের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। কারণ অন্য যে-কোনো পরীক্ষায় দু-একজনের ইয়ারবক্সী ফেল মারেনই মারেন— নিতান্ত পরশ্ৰীকান্তর এবং বিয়-সন্তোষী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারোরই কোনো পরীক্ষা পাশ নিরঙ্কুশ আনন্দদায়ক হয় না—এ-পরীক্ষায় কিন্তু সবাই পাশ, সবাই রাজা। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আজ স্বাধীন হলেন, আপনিও হলেন, আমিও হলুম!
কিন্তু প্রশ্ন অতঃ কিম? অবশ্য বলতে পারেন। পরীক্ষা পাশ করে জ্ঞানার্জন হল এবং জ্ঞানার্জন স্বয়ংসম্পূর্ণ, আপন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত। এর পর কিছু না করলেও কোনো আপত্তি নেই। এটা একটা উত্তর বটে কিন্তু কোনো জিনিস একদম কোনো কাজে লাগল না। এ-কথাটা ভেবে কেমন যেন সুখ পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, ইট ইজ বেটার টু ব্রেক দি হার্ট ইন লাভ দেন ডু নাথিং উইথ ইট’–স্বাধীনতাটা কোনো কাজে লাগাব না একথা ভেবে মন কেমন যেন সুখ পায় না; বাসনা হয়, দেখাই যাক না, রাজনৈতিক স্বরাজের মই চড়ে আরো পাঁচ রকমের স্বরাজ হস্তগত হয় কি না; এ লোভ সকলেরই থাকবে সে-কথা হলপ করে বলা যায় না, কিন্তু অন্ততপক্ষে এ তত্ত্বটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, পাশের পর লেখা-পড়া বন্ধ করে দিলে জ্ঞান যে রকম কপূরের মতো বিনা কারণেই উবে যেতে থাকে, স্বাধীনতাটাকেও তেমনি চালু না রাখলে ক্ৰমে ক্ৰমে সেও তার রূপ বদলাতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পরমুহূর্তেই যদি বেধড়ক ধর-পাকড় আরম্ভ করে দেন, মনে মনে ভাবেন পাঁচটা লোকের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেই পাঁচশ লোকের স্বাধীনতার বাঁচা তো হয়ে যাবে। কিংবা যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে না ঝোলান। তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বরাজ লাভটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আগেভাগে হলফ করে কিছু বলা যায় না।
হিটলারের পূর্বেও জর্মনি স্বাধীন ছিল কিন্তু জর্মনিকে সর্বাঙ্গসুন্দর স্বাধীনতা দিলেন হিটলার। লেনিনের পূর্বে রাশার জনসাধারণ স্বাধীনতার স্বাদ পায় নি, লেনিন এক ধাক্কায় গোটা দেশটাকে অনেকখানি এগিয়ে দিলেন। এখন আবার স্তালিন দেশটাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন যে এর পর কি হয় না হয় বলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনিও হিটলারের গতি লাভ করবেন নাকি?
কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, আমাদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো উপায় নেই-কিছু একটা করতেই হবে। স্বাধীনতার ঘোড়া চড়ি আর নাই চড়ি সেটাকে অন্তত বাঁচিয়ে রাখার জন্য দানা-পানির খর্চা হবেই হবে।
আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকখানি বিলিতি ছিল বলে আমাদের স্বরাজলোভও অনেকখানি বিলিতি কায়দায় হয়েছে। এখনও আমাদের লাটবেলাটরা বিলিতি কায়দায় লঞ্চ-ডিনার খাওয়ান, পেরটি দেখেন, সেলুট নেন, এডিসি ফেডিসি কত ঝামেলা, কত বখেড়া। তাই স্বাধীনতা নিয়ে কি করব কথাটা উঠলেই গুণীরা বলেন, ‘ইয়োরোপ কি বলছে, কান পেতে শোনো তো; তারপর বিবেচনা করে ভালো-মন্দ যা হয় একটা কিছু করব।’
ইয়োরোপ কি বলছে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো ধোঁকা নেই। ইয়োরোপ বলছে, ‘হয় মার্কিন ইংরেজের ডিমোক্রেসি গ্রহণ করে তাদের দলে যোগ দাও, নয়। লালরক্ত মেখে রুশের সঙ্গে এক হয়ে যাও। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।’
ক্ষীণকণ্ঠে কেউ কেউ বলেন, ‘কেন? টিটো?’
উত্তরে শুনি অট্টহাস্য। টিটো ইংরেজ বন্দুক-কামান কেনা-বেচার সমঝওতাও নাকি হয়ে গিয়েছে কিংবা হব-হব করছে। টিটো মিয়ার তৃতীয় পন্থা’ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার মতো তিন দিনও টিকল না। তাকেও আস্তে আস্তে মার্কিন-ইংরেজের আস্তিন পাকড়ে এগোতে হচ্ছে।
এর পর আর কোন সাহসে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের কথা তুলি?
এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়োরোপীয় সাহিত্যিক, চিত্রকর, কবি, দার্শনিকদের নিরঙ্কুশ নৈরাশ্যবাদ। ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন, ইতালি যে কোনো মাসিক খুললেই দেখতে পাবেন ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিই মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, ‘কোনো পন্থাই তো দেখতে পাচ্ছি নে-মার্কিনের দেখানো পথ মনঃপূত হয় না, রুশের পথই বা ধরি কি প্রকারে? মার্কিন ইংরেজের ‘ডিমোক্রেসি’ এমনিতেই শোষণ-পহী, তার উপর আমরা যদি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কমুনিজমকে নির্মূল করে দি তাহলে এখনো তারা রুশ জুজুর ভয়ে যেটুকু সমঝে চলত, চাষামজুরকে দুমুঠো অন্ন দিত। তাও আর দেবে না। আর রুশের কলমা পড়ে যদি মার্কিন ইংরেজকে সাবড়ে দিই তাহলে স্তালিনকে ঠেকাবে কে? যুগ যুগ সঞ্চিত ইয়োরোপের তাবৎ সভ্যতা তাবৎ সংস্কৃতিকে তো তিনি ‘বুর্জেয়া’ বলে নাকচ করে দিয়েছেন, এমন কি তাঁরা আপনজন ভাৰ্গ, ভাভিলফ, কলৎসফ হয় ‘পেনশনে’ নয় নির্বাসনে কিংবা মাটির নীচে। স্তালিন যদি বিশ্বজয় করতে পারেন তবে এ-দুনিয়াতে বাইবেল-কুরান, বেদ-পুরাণ তো থাকবেনই না, প্লাতো-শেকসপীিয়র থাকবেন। কিনা তাই নিয়ে অনায়াসে জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে। আণ্ডা-মাখনের ছয়লাফ হয়তো হবে, কিন্তু এই পৃথিবীর লোক প্লাতে শেকস্পীয়র পড়তে পাবে না। শুনে স্তালিনী কলম পড়তে কিছুতেই মন মানে না।’
এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্ৰীষ্টধর্মের প্রতি এদের নৈরাশ্যের অনুযোগ। একমাত্র পেশাদারী পাদ্রি-পুরোত ছাড়াইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ আর এ-বিশ্বাস করেন না যে প্ৰভু যীশুর সাম্যের বাণী বিশ্বসমস্যার সমাধান করতে পারবে। একদিন সে-বাণী দাসকে মুক্তি দিয়েছিল, অত্যাচারকে শান্ত করতে পেরেছিল, জড়লোক থেকে অধ্যাত্মলোকের অনির্বাণ দীপশিখার চিরন্তন দেওয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ সে বাণী ভার্টিকানের আপনি দেশেই লুণ্ঠন অগ্নিবর্ষণ বন্ধ করতে পারছে না।
ইয়োরোপ মরা ঘোড়ার মতো পড়ে আছে। ধর্মের চাবুকে সে আর খাড়া হবে না। অতএব? অতএব কোনো দিকেই যখন আর কোনো ভরসা নেই তখন যা-খুশি একটা বেছে নাও। আর দয়া করে আমাদের শাস্তিতে মরতে দাও, আর তাও যদি না করতে দাও তবে আত্মহত্যা করতে দাও। রুশিয়া এবং পশ্চিম-ইয়োরোপে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভিতরই আজ বেশি।
***
আমরা যদি হটেনটট হাতুম তাহলে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা থাকতো না। আত্মহত্যা ছাড়া—অসভ্যদের ভিতর আত্মহত্যার সংখ্যা অতি নগণ্যও বটে—অন্য যে-কোনো দুটো পন্থার ভিতরে একটা বেছে নিয়ে দুৰ্গা’ বলে ঝুলে পড়তুম। তারপর যা-হবার মত। (কিছুটা যে হয়েছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। কম্যুনিস্টরা তো আছেনই, আরেক দল যে রুশের বিরুদ্ধে ঝটপট শক্ৰতা জানিয়ে মার্কিন কল-কব্জা হাতিয়ে এ-দেশটা শোষণ করতে চান সে তত্ত্বটাও আমাদের অজানা নয়।)
‘ধন্য সেই জাত, যার কোনো ইতিহাস নেই।’ সে নিৰ্ভয়ে যা-কিছু একটা বেছে নিতে পারে।
কিন্তু দুৰ্ভাগ্যই বলুন, আর সৌভাগ্যই বলুন আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে। সে ঐতিহে্যু আমরা শ্ৰদ্ধা হারাই নি-হয়তো তার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী শাসনের ফলে আমরা সে ঐতিহ্য অনুযায়ী চলবার সুযোগ এ যাবৎ পাই নি।
কিন্তু যতদিন সে-শ্রদ্ধা আমাদের মনে রয়েছে ততদিন তো আমরা বিগত যৌবনা অরক্ষণীয়ার মতো নিরাশ হয়ে গিয়ে মার্কিন কিংবা রুশের গলায় মালা পরিয়ে দিতে পারি। নে। স্বরাজের জন্য যারা জেল খাটল, প্ৰাণ দিল তাদের অনেকেই তো মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিল ভারতবর্ষের লুপ্ত ঐতিহ্য উদ্ধার করে তারই আলোকে ভবিষ্যতের পথ বেছে নেব, এমন কি গোপনে গোপনে হয়তো এ দম্ভও পোষণ করেছিল যে বিশ্বজনকেও সেই ‘আলোকমাতাল স্বৰ্গসভার মহাঙ্গনে’ নিমন্ত্রণ করতে পারবে। কৃষ্ণের দেশ, বুদ্ধের দেশ, চৈতন্যের দেশ আজি কপৰ্দকহীন, দেউলে, একথা মন তো সহজে মেনে নিতে চায় না।
কিন্তু সেখানে আরেক বিপদ। ঐতিহ্যের কথা তুললেই আরেক দল উল্লসিত হয়ে বলেন, ‘ঠিক বলছি, চলো, আমরা বেদ-উপনিষদের সত্যযুগে ফিরে যাই।’
কোনো বিশেষ সত্যযুগে ফিরে যাওয়ার অর্থই মেনে নেওয়া যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কোনো জিনিস নেই, সেই যুগকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরার অর্থই হল এ-কথা মেনে নেওয়া যে আমরা যুগ যুগ ধরে শুধু অবনতির পথেই চলে আসছি এবং নূতন জীবন, নবীন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার মতো কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই এঁরা তখন সেই বিশেষ ‘সত্যযুগে’র আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম (এমন কি কুসংস্কার পর্যন্ত, কারণ আমরা বিশেষ কোনো সর্বাঙ্গসুন্দর সত্যযুগে বিশ্বাস করিনে বলে সব যুগেই কিছু না কিছু কুসংস্কার মুঢ়তা ছিল বলে ধরে নিই) পদে পদে অনুসরণ অনুকরণ করতে লেগে যান, তখন জিগির ওঠে, ইয়োরোপীয় সব কিছু বর্জন করো, মার্কিন রুশের গা ছুঁয়েছ কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ছড়াও চতুর্দিকে গোবরের জল, ঠেকও তাই দিয়ে শুদ্ধ ‘ভারতীয়-সংস্কৃতি’–কে ‘অস্পৃশ্যের পাপস্পর্শ থেকে’।
এঁরা গড়ে তুলতে চান আবার সেই অচলায়তন’ যার অন্ধ প্রাচীর ভেঙে ফেলবার জন্য কবিগুরু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নবযুগের প্রতীক নূতন ‘ডাকঘর’ যার ভিতর দিয়ে রুগ্ন অমলকে বাণী পাঠাবেন প্রাচীন রাজা, যিনি জনগণের অধিনায়ক, ভারতভাগ্য-বিধাতা।
মার্কিন না রুশ না, এমন কি ভারতীয় কোন বিশেষ সত্যযুগ’ও না-এসব এড়িয়ে বাঁচিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের চলিষ্ণু সদাজাগ্রত শাশ্বত সত্যধর্মের পথে আমাদের চালাবেন কে? সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব, আদর্শে আদর্শে সংঘাত, ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে সংগ্রাম, এর মাঝখানে শান্তসমাহিত হয়ে ধ্রুব সত্যের সন্ধান দেবেন কে?
তিনি এলে আমরা তাকে চিনতে পারব তো? আমরা মনে হয়। পারব। কারণ তিনি কোন ভাষায় তার বাণী প্রচার করবেন তার কিছুটা সন্ধান আমরা পেয়ে গিয়েছি—তিনি স্বীকার করে নেবেন প্রথমেই জনগণমন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে, তার উদার বাণীতেও অহরহ প্রচারিত থাকবে সেই আহ্বান যে আহ্বানে সাড়া দেবে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখজৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্ৰীষ্টান, তার কণ্ঠে শুনতে পাবো সেই চির-সারথির রথচক্ৰঘর্ঘর, যিনি পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার উপর দিয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদিগকে এই নবযুগের অরুণোদয়ের সামনে।
শত মূঢ়তার মাঝখানে যে আমরা আজ কোটিকণ্ঠে ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে স্বীকার করে নিলুম-জাতীয়-সঙ্গীত নির্বাচনে পথভ্রান্ত হইনি-এ বড় কম আশার কথা নয়।
দিনেন্দ্রনাথ
‘দেশে’র ৪১শ সংখ্যা শ্ৰীযুক্ত প্ৰভাতচন্দ্র গুপ্ত স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে দিনেন্দ্ৰভক্ত, দিনেন্দ্ৰ-সখাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গুপ্ত মহাশয় দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এবং তথ্য, দিনেন্দ্রনাথের মধুর, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল হৃদয়ের এ বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার মনে দিনেন্দ্ৰনাথের যে ছবি আছে সেটি হুবহু মিলে গেল। একাধিকবার ভেবেছি দিনেন্দ্ৰনাথ সম্বন্ধে এত অল্প লোকই লিখেছেন যে তাঁর প্রতি আমার শ্ৰদ্ধা জানিয়ে আমার যেটুকু জানা আছে তাই লিখে ফেলি, কিন্তু প্রতিবারেই মনে হয়েছে, দিনেন্দ্র-জীবন আলোচনা করার শাস্ত্ৰাধিকার আমার নেই। গুপ্ত মহাশয় এখন আমার কর্তব্যটি সরল করে দিলেন। আমার বক্তব্যের কোনো কথা যদি গুপ্ত মহাশয়ের কাজে লেগে যায়, তবে আমি শ্রমসাফল্যের আনন্দ পাব।
স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে যে বক্তৃতা দিতেন, তা অতুলনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি, যেদিনকার উপাসনা দিনেন্দ্ৰনাথের সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ হত, সেদিন সে সঙ্গীত যেন আমাদের মনে করে রবীন্দ্ৰনাথের উপাসনার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত এবং উন্মুখ করে তুলত। দিনেন্দ্রনাথের বিশাল গভীর কণ্ঠ আমাদের হৃদয়মন ভরে দিত, তার পর সমস্ত মন্দির ছাপিয়ে দিয়ে ভাঙা-খোয়াই পেরিয়ে যেন কোথা থেকে কোথা চলে যেত। তাই আমার সব সময় মনে হয়েছে দিনেন্দ্ৰনাথের কণ্ঠ একজনকে শোনাবার জন্য, এমন কি একটা সম্পূর্ণ আসরকেও শোনাবার জন্য নয়, তার কণ্ঠ যেন ভগবান বিশেষ করে নির্মাণ করেছিলেন সমস্ত দেশের জনগণকে শোনাবার জন্য তাই বোধ হয় তার কণ্ঠে যে রকম ‘জনগণমন অধিনায়ক’ গান শুনেছি আজ পর্যন্ত কারো কণ্ঠে সেরকম ধারা শুনলাম না।
এরকম গলা এ দেশে হয় না—এ গলার ভালুম পেলে ইতালির শ্রেষ্ঠতম অপেরাগাইয়ে জীবন ধন্য মনে করেন।
হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, মন্দিরে দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত যেন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠতর ধর্মব্যাখ্যানে অনুপ্রাণিত করেছে।
একথা সবাই জানেন, দিনেন্দ্রনাথ যে শুধু গায়কই ছিলেন তাই নয়, তিনি অতিশয় উচ্চাদরের সঙ্গীতরসজ্ঞও ছিলেন। কি উত্তর কি দক্ষিণ, কি ইয়োরোপীয় সর্বসঙ্গীতে সর্ববাদ্যের খবর তিনি তো রাখতেনই-তার উপর তিনি জানতেন কি করে গায়ক এবং যন্ত্রীকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য টেনে বের করে আনতে হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর হয়ে গিয়েছে, তাই আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় সে গুণীর নাম ছিল সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী, পিঠাপুরুম মহারাজের বীণকার-তিনি এসেছেন রবীন্দ্রনাথকে বীণা শোনাতে। রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ উদগ্ৰীব হয়ে বসেছেন; তার পর আরম্ভ হল বীণাবাদন।
আমার সন্দেহ হয়েছিল দক্ষিণের গুণীর মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল, উত্তর ভারতের শান্তিনিকেতন তাঁর সঙ্গীত সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে কি না। দশ মিনিট যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ যেমন যেমন তাঁদের সূক্ষ্ম রসানুভূতি ঘাড় নেড়ে, মৃদু হাস্য করে বা বাহবা বলে প্রকাশ করতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গমেশ্বর বুঝতে পারলেন তিনি যে সমঝদার শ্রোতার সামনেই বাজাচ্ছেন তাই নয়, এ রকম শ্রোতা তিনি জীবনে পেয়েছেন। কমই। সে রাত্রে কটা অবধি মজলিস চলেছিল আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে শান্তিনিকেতনের ‘খাবার ঘণ্টা’র অনেক পর অবধি—বারোটা হতে পারে, দুটাও হতে পারে।
সে যুগে ইয়োরোপ থেকেও বহু কলাবিৎ আসতেন। রবীন্দ্রনাথকে গান কিংবা বাজনা শোনাতে। দুজনকে স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু নাম ভুলে গেছি। একজন ডাচ মহিলা গাইয়ে (বিনায়ক রাও এর নাম স্মরণ করতে পারবেন) এবং অন্যজন বেলজিয়ান বেহালা-বাজিয়ে। ডাচ মহিলাটি খুব বেশি দিন আশ্রমে থাকেন নি, কিন্তু বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে একদম জমে যান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বাজিয়ে যেতেন-ভদ্রলোক দিনে অস্তুত বারো ঘণ্টা আপন মনে, একা একা, বেহালা বাজাতেন–আর দিনেন্দ্রনাথ তার সূক্ষ্মতম কারুকার্যের সময় মাথা নড়ে নেড়ে রসবোধের পরিচয় দিয়ে তার উৎসাহ বাড়াতেন।
বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখেছিলেন-তার অন্যতম, সিগার বর্জন করে গড়গড়া পান। আশ্রম ছাড়ার দিন ভদ্রলোক দুঃখ করে আমাকে বলেছিলেন, ‘দেশে যেতে মন চাইছে না, সেখানে তামাক পাব কোথায়?’ যদিস্যাৎ পেয়ে যান। সেই আশায় ভদ্রলোক তার আলবোলাটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।
দিনেন্দ্ৰনাথ সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ সমঝদার ছিলেন। প্ৰাপ্তবয়সে তিনি ফরাসীও শিখেছিলেন এবং স্বচ্ছন্দে ফরাসী উপন্যাস পেতে পারতেন। ওদিকে ভারতের সংস্কৃতি ইতিহাসের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রেম। তাই কি লেভি, কি উইনটারনিৎস সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদ্যতা। বিদেশীকে কি করে খানা খাইয়ে, আড্ডা জমিয়ে, সঙ্গীতের চর্চা করে, সৌজন্য ভদ্রতা দেখিয়ে-আমি একমাত্র দিনেন্দ্রনাথকেই চিনি যিনি পৃথিবীর সকল জাতের লোকেরই ম্যানারস এটিকেট জানতেন—তার দেশের কথা ভুলিয়ে দেওয়া যায় এ কৌশল তাঁর যা রপ্ত ছিল এর সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। তাই তাঁর বাড়ি ছিল বিদেশীদের কাশীবৃন্দাবন। দিনেন্দ্ৰনাথ গাইতে পারতেন, বাজাতে পারতেন, অন্যের গানবাজনার রস চাখতে পারতেন এ-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি; তদুপরি তিনি ছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্ৰজ্ঞ। এ বড় অদ্ভুত সমন্বয়। শাস্ত্রজ্ঞের রসবোধ কম, আবার রসিকজন শাস্ত্রের অবহেলা করে—দিনেন্দ্ৰনাথ এ নীতির ব্যত্যয়-শাস্ত্রের কচকচানি তিনি ভালবাসতেন না। কিন্তু সঙ্গীতের বিজ্ঞানসম্মত চর্চার জন্য যেখানেই শাস্ত্রের প্রয়োজন হত, তিনি সেখানেই সত্য শাস্ত্ৰ আহরণ করে ছাত্রের সঙ্গীতচর্চা সহজ সরল করে দিতে জানতেন।
আমাদের ঐতিহ্যগত রাগপ্রধান সঙ্গীতচর্চার জন্য প্রাচীন অর্বািচীন বহু শাস্ত্ৰ আছে, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে সঙ্গীতের যে নূতন ভুবন সৃষ্টি করে দিলেন, তার রহস্য ভেদ করার জন্য কোনো প্ৰমাণিক শাস্ত্র নেই। এ-শাস্ত্র নির্মাণ করার অধিকার একমাত্র দিনেন্দ্ৰনাথেরই ছিল। বহু অনুনয়-আবেদন করার পর তিনি সে শাস্ত্র রচনা করতে সম্মত হলেন।
কয়েকটি অধ্যায় তিনি লিখেছিলেন। সেগুলি অপূর্ব। শুধু যে সেগুলিতে রবীন্দ্ৰসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত দর্শনে’র সন্ধান মেলে তাই নয়, সেগুলিতে ছিল ভাষার অতুলনীয় সৌন্দর্য অমিত ঝঙ্কার-সে ভাষার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি একমাত্র ‘কাব্যের উপেক্ষিতা’র ভাষা।
এ শাস্ত্ৰ তিনি কখনো সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন। কিনা জানিনে। হয়তো আমার ভুল, কিন্তু প্ৰথম অধ্যায়গুলো শুনেই আমার মনে হয়েছিল। এ ছন্দে শেষরক্ষণ করা সহজ কর্ম নয়। এর জন্য যতখানি পরিশ্রমের প্রয়োজন, দিনেন্দ্ৰনাথের হয়তো ততখানি নেই।
আমি দিনেন্দ্রনাথের নিন্দে করছি নে। কিন্তু আমি জানি তিনি গান গাইতে, বাজনা বাজাতে, গানবাজনা শুনতে, সাহিত্যরস উপভোগ করতেন, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে, আড্ডা জমাতে, বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াতে, বিদেশীদের আদর-আপ্যায়ন করাতে এত আনন্দ পেতেন যে কোনো প্রকারের কীর্তি নির্মাণ করাতে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ পর্যাম্বুখ, নিরঙ্কুশ বীতরাগ।
নাই বা হল সে শাস্ত্র সে কীর্তি গড়া! আজ যদি দিনেন্দ্ৰ-শিষ্যেরা আপন আপন নৈবেদ্য তুলে ধরেন, তবে তার থেকেই নূতন শাস্ত্ৰ গড়া যাবে।
দিস ইয়োরোপ
গিরিজা মুখুজ্জে দেশে থাকতে বার দুই জেলে যান—সে কিছু না, নস্যি। (কেন বলছি, বাকিটুকু পড়লেই বুঝতে পারবেন)। তারপর ছিটকে গিয়ে লন্ডন, সেখান থেকে প্যারিস। দিব্য আছেন, সরবন যান, ফরাসী গুণীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, দু পয়সা কামানও বটে। এমন সময় দেখা গেল, জর্মনরা প্যারিসের ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। মুখুজ্জে গুটিকয়েক ফরাসী আত্মজনের সঙ্গে আরো সব লক্ষ লক্ষ ফরাসিদের মতো দক্ষিণের পথ ধরলেন। পায়ে হেঁটে, মালবোঝাই বাইসিকেল কিংবা হাত-গাড়ি ঠেলে ঠেলে যখন ক্ষুধাতৃষ্ণা, ক্লান্তিতে ভিরমি যাবার উপক্রম (ওদিকে মনে মনে ভাবছেন, জর্মনদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন), তখন হঠাৎ মালুম হল, জর্মন বাহিনী তাঁকে পিছনে ফেলে রাতারাতি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তখন সামনে পিছনে সবই সমান; ফিরে এলেন প্যারিস।
মুখুজ্জে ভারতীয়, কাজেই ইংরেজের দুশমন। কিন্তু তাহলে কি হয়-পাসপোর্ট যে পাকাপোক্ত ইস্টাম্পো মারা রয়েছে, মুখুজ্জে ব্রিটিশ প্রজা, অর্থাৎ তিনি জার্মানির শত্রু। কাজেই যদিও পাদমেকং ন গচ্ছমি করে আপনি কুঠুরিতে সুবো।–শাম ঘাপটি মেরে বসে থাকেন, তবু।
একদা কেমনে জানি ভারতীয় মহাশয়
পড়িলেন ধরা, আহা, দূরদৃষ্ট অতিশয়।(১)
জর্মন পুলিশের তদারকিতে ফরাসী জেলখানায় মুখুজ্জে তখন ইস্টদেবতার নাম জপ। করতে লাগলেন। সে-জেলে ইংরেজের শত্ৰু-মিত্র বিস্তর ব্রিটিশ’ প্রজার সঙ্গে তার যোগাযোগ হল। তার বর্ণনাটি মনোরম।
কিছুদিন পর জেল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।
তখন নাম্বিয়ার তাকে বললেন, তার সঙ্গে বার্লিন যেতে। সেখানে গিয়ে দেখেন, সুভাষচন্দ্ৰ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হরেক রকম তরিকত-তত্ত্বতাবাশ আরম্ভ করে দিয়েছেন। মুখুজ্জেকে ‘আজাদ হিন্দ’ বেতারে বেঁধে দেওয়া হল নানা প্রকারের ব্রডকাস্টের জন্যে। সুভাষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যোগাযোগ হল। গ্র্যান্ড মুফতির সঙ্গেও বিস্তর দহরম মহরাম হল।
সুভাষ সম্বন্ধে মুখুজ্জে অনেক কিছু লিখেছেন। উপাদেয়।
তারপর সুভাষ দেখলেন, বার্লিনে থেকে কাজ হবে না। ওদিকে ইংরেজ সিঙ্গাপুরে শিঙে ফুঁকেছে। জাপানীরা বর্মায় ঢুকছে। সুভাষ চলে গেলেন জাপান। এদিকে ‘আজাদ হিন্দ’ বেতার দাঁড়কচা মেরে গেল। মুখুজ্জেরা কিন্তু ক্ষান্ত দেন নি।
তারপর জর্মনির পতন আরম্ভ হল। বোমার ঠেলায় বার্লিনে কাজ করা দায়। তাবৎ ভারতীয়কে সরানো হল হল্যান্ডে; সেখান থেকে ‘আজাদ হিন্দ’র বেতোরকর্মচালু থাকল বটে, কিন্তু মুখুজ্জেরা বুঝলেন, সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারপর প্রায় সবাই একে একে ফিরে এলেন বার্লিন। সেখান থেকে মুখুজ্জে গেলেন দক্ষিণ-জার্মনিতে। ইতিমধ্যে রাশানরা ঢুকল বার্লিনে।
এবারে তিনি আইনত রাশার শত্রু। কারণ রাশার মিত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি বিস্তর বেতার বক্তৃতা ঝেড়ে বসে আছেন। আইনত তিনি অ্যামেরি, হো হো’র সমগোত্র। কাজেই পালাতে হলে নিরপেক্ষ’ সুইটজারল্যান্ডে। এক দরদী জর্মন সীমান্ত পুলিশই তাকে বাতলে দিলে কি করে নিযুতি রাতে রাইন নদী সাঁতরে ওপারে যাওয়া যায়।
আমরা ভাবি সুইসরা বড়ই নিরপেক্ষ মোলায়েম জাত। মুখুজ্জে সেখানে যে বেইজাতি আর লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে গেলেন, তার বর্ণনা আমি আর এখানে দিলুম না।
সুইসরা মুখুজ্জেকে আত্মহত্যার দরজায় পৌঁছিয়ে হঠাৎ একদিন প্রায় ‘কানে ধরে’ ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল জর্মনিতে। জর্মনির যে অঞ্চলে তাঁকে ফেরত-ডাকে পাঠানো হল, সেটি ফরাসীর তীবেতে। কাজেই তাকে পত্রপাঠ গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু মুখুজ্জে যখন কমান্ডান্টিকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি জর্মনিতে যা কিছু করেছেন সে শুধু ‘পাত্রি’র (দেশের) জন্য, তখন ফরাসীরা-আর এ শুধু ফরাসীরাই পারে—মুখুজ্জের বিগত জীবনটা যেন বেবাক ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, খেতে পরতে দিল। বলল, ‘তুমি যখন দিব্য ফরাসিজর্মন জানো, তখন আমাদের সঙ্গে থেকে কাজ করো না কেন?’ তাই সই। ব্যবস্থাটা স্থানীয় জর্মনদেরও মনঃপূত হল—অবিশ্যি বিজয়ী ফরাসীরা তখন তার থোড়াই পরোয়া করতকারণ মুখুজ্জে তাদের সামনে ‘দম্ভী বীরে’র মূর্তিতে দেখা দেন নি।
তারপর সেই ফরাসী রেজিমেন্ট দেশে চলে গেল। মুখুজ্জের আবার জেল। ইংরেজ তখন অ্যামেরি হো হো’র মতো মুখুজ্জেকে পেলে তাঁকেও ঝোলায়।
কিন্তু ঝোলাবার সুযোগ পায় নি। ফরাসীরা মুখুজ্জেকে ইংরেজের হাতে তুলে দেয় নি। তারপর স্বরাজ হয়ে গেল। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এল।
***
কিন্তু বইখানা মুখুজ্জের আত্মজীবনী নয়। বইটিতে মুখুজ্জে ইয়োরোপ দেখেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা পটপরিবর্তনের সামনে, পয়লা সারিতে বসে। উত্তম বই।(২)
——-
(১) সুকুমার রায়ের অচলিত কবিতা।
(২) S. Girija Mukherjee, This Europe. Saraswaty library, Calcutta.
নন্দলালের দেওয়াল-ছবি
তুর্ক-নাচন নাচেন নন্দবাবু
চতুর্দিকে ছেলেরা সব কাবু।
তুলির গুক্তিা ডাইনে মারেন, মারেন কাভু বাঁয়ে
ঘাড় বাঁকিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে, দাঁড়িয়ে এক পায়ে।
অষ্টপ্রহর চর্কীবাজী কীর্তি-মন্দিরে
ছেলেরা সব নন্দলালকে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে।
হচ্ছে ‘নটীর পূজা’
রানীর সঙ্গে হল নটীর পূজা নিয়ে যুঝা।
বরাঙ্গনা ভিক্ষু নটীর নৃত্যচ্ছন্দ ধূপ—
তুলির আগুন পরশ পেয়ে নিল আবার সেই অপরূপ রূপ
—বহু যুগের পরে—
চৈত্যভবন ভরে।
—সন্ধ্যাকাশে ফোটে যেন তারার পরে তারা—
হেথায় সেতার কঁপে ভীরু, হোথায় বীণার মীড়
আধফোটা গুঞ্জরণের ভিড়
তার পিছনে মৃদু করুণ-বাঁশি
গুমগুমিয়ে থেকে থেকে উঠছে ভেসে খোল-মৃদঙ্গর হাসি।
এ যেন সুন্দরী–
প্রথমেতে নীলাম্বরী পরি,
তিলোত্তমা গড়ে নন্দলাল।
চিত্রপটে কিন্তু নটী ফেলে অলঙ্কার
শুনি যেন বলে চিত্রকার–
“তথাগতের দয়ায় যেন তেমনি ঘুচে তোমা সবার সকল অহঙ্কার।”
সাদামাটার রক্তবিহীন ঠোঁটে
লজ্জা সোহাগ ফোটে,
পাংশু দেয়াল আনন্দে লাল নন্দলালের লালে
তুলির চুমো যেই না খেলো গালে।*
—–
* শ্ৰীযুক্ত নন্দলাল বসুর বরদারাজ্যের ‘কীর্তি-মন্দিরে’ রবীন্দ্রনাথের ‘নটীর পূজা’র ফ্রেস্কো ছবি আঁকিবার সময় লেখক কর্তৃক এক বান্ধবীকে আসিয়া দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্ৰ।
নাগা
৩১শে আগস্ট সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহয়াহর(১) লাল নেহরু বলেন যে, গত ২৪শে মে একদল নাগা : ভারতীয় নাগা-অঞ্চলে হানা দেয় ও ৯৩টি মুণ্ড কেটে নিয়ে চলে যায়।
আসামে মিরি, মিশমি, আবার, আকা, দফলা, কুকী, গারো, লুসাই, খাসী, নাগা ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে। এদের ভিতর খাসী, লুসাই, গারোয়া এবং আরো কয়েকটি জাতি বড়ই ঠাণ্ডা মেজাজের, এবং সবচেয়ে মারাত্মক নাগারা। এরা এখনো পরমানন্দে নরমাংস ভক্ষণ করে এবং কে কতটা শৌৰ্যশালী তার বিচার হয় কে কটা মুণ্ডু কাটতে পেরেছে তাই দিয়ে।
নাগা পাহাড়ের যে অংশুটুকু ইংরেজ দখল করে সেখানে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর মিশনারি যায় এবং ফলে অনেক নাগা খ্ৰীষ্টান হয়ে যায়। মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও ইংরেজের আইনকানুনের ভয়ে ব্রিটিশ নাগারা বড় অনিচ্ছায় মানুষ কেটে কেটে খাওয়া বন্ধ করে; কিন্তু স্বাধীন ও বমী নাগারা এসব ‘ম্নেচ্ছ-সংস্কারে’র কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে সুযোগ পেলেই ব্রিটিশ নাগা অঞ্চলে হানা দিয়ে মুণ্ডু কেটে নিয়ে যেতে থাকে।
বিশেষ করে ব্রিটিশ (বর্তমান ভারতীয়) অঞ্চলেই এরা হানা দেয় কেন?
তার একমাত্র কারণ ব্রিটিশ আইন করে-এবং সে আইন ভারতীয়রাও চালু রেখেছেন-ব্রিটিশ নাগাদের ভিতরে এক গ্রাম অন্য গ্রামকে হানা দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করে দেয়। অবশ্য এ আইন নাগারা চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নেয় নি-বিস্তর মার খাওয়ার পর অতি অনিচ্ছায় তারা হানাহানি বন্ধ করে। ফলে তারা নিবীর্য ও শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে হানাহানির জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন সেগুলো লোপ পেতে থাকে।
ওদিকে স্বাধীন নাগারা দেখল। এ বড় উত্তম ব্যবস্থা। আপসে তারা মাঝে মাঝে হানাহানি করে বটে, কিন্তু সেখানে যেমন অন্যের মুণ্ডুটি কাটবার সম্ভাবনা আছে ঠিক তেমনি নিজের মুণ্ডুটি কাটা যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনাও আছে, কারণ উভয় পক্ষই উদয়াস্ত লড়াইয়ের পায়তারা কষে, তাঁর চোখ রাখে, ধনুকের ছিলা বদলায়। অপিচ ব্রিটিশ নাগারা লড়াই করতে ভুলে গিয়েছে, তীরন্ধনুক যা আছে তা দিয়ে হানাহানি করা যায় না। এদের হানা দিলে প্ৰাণ যাবার ভয় নেই, গোলায় মজুদ ধান লুট করা যায়। আর শূয়ার ছাগল তো নিতান্তই ফাউ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, একগাদা মুণ্ড কপোকপ কেটে নিয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি চলে যাওয়া যায়। অন্ততপক্ষে একটা মুণ্ডু না দেখাতে পারলে স্বাধীন নাগা অঞ্চলে বউ জোটে না; কাজেই নাগা সম্বরণদের গত্যন্তর কোথায়?
ভারতীয় নাগারা ফরিয়াদ করে আমাদের বলে, ‘হানাহানি বন্ধ করে দিয়ে তোমরা আমাদের নিবীৰ্য করে ফেলেছি। তাই সই। কিন্তু তার ঝুকিটা কি তোমাদেরই নেওয়া উচিত নয়? স্বাধীন নাগারা যখন আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে তখন আমরা আত্মরক্ষা করতে অক্ষম। তোমাদের কি তখন কর্তব্য নয় পুলিশ সেপাই রেখে আমাদের বাঁচানো?’
অতি হক কথা। কিন্তু প্রশ্ন, এ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় কি প্রকারে? আমাদের সেপাইরা যে নাগাদের ডরায় তা নয়, কারণ নাগাদের হাতে বন্দুক থাকে না। গোটা দুক্তিন মেসিনগান দিয়েই এক পাল নাগাকে কাবু করা যায়, কিন্তু বেদনাটা তখন সেখানে নয়। মুশকিল হচ্ছে এই স্বাধীন নাগারা হানা দেবার পূর্বে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়ে শুভাগমন করে না এবং আমাদের পক্ষেও প্রতি পাহাড়ের চুড়োয় সেপাই মোতায়েন করা সম্ভব নয়।
নাগারা দল বেঁধে গাঁ বানিয়ে সমতলভূমিতে বসবাস করে না। তারা থাকে পাহাড়ের চূড়োয় চুড়োয় এবং সে চুড়োগুলোর উচ্চতা তিন থেকে ছ হাজার ফুট। কাজেই এক পাহাড়ের চূড়ো থেকে যদি দেখাও যায় যে অন্য চুড়ো আক্রান্ত হয়েছে। তবু সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতেই সব কেচা খতম হয়ে যায়।
তবে কি নাগাদের আপনি হাতে কিছু কিছু বন্দুক-টন্দুক দেওয়া যায় না? সেখানে মুশকিল হচ্ছে, নাগাদের ঠিক অতটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ বন্দুক পেলে তারা সোল্লাসে অবিচারে অন্য নাগাদের আক্রমণ করবে। তাহলে সে একই কথায় গিয়ে দাঁড়ালো।
নাগারা এই ব্যবস্থাটাই চায়। তারা বলে, তোমরা যখন আমাদের বাঁচাতে পারছি না। তখন আমরাই আপন প্ৰাণ বাঁচাই। এটাতেও আমাদের মন সাড়া দেয় না।
আচ্ছা, তবে কি আমাদের সৈন্যরা স্বাধীন নাগা অঞ্চল আক্রমণ করে তাদের বেশ কিছু ডাণ্ডা বুলিয়ে দিতে পারে না?
পারে। তবে তাতেও ঝামেলা বিস্তর।
——–
(১) বাঙলাতে সাধারণত জওহর’ লেখা হয় এবং এ ভুল সংশোধন করা উচিত। জওহর’ কথাটি ফার্সীতে একবচন এবং অর্থ বাংলাতে যা তাই। ‘জওয়াহর’ কিংবা ‘জওয়াহির’ শব্দটি ‘জওহর’ শব্দের আরবী ব্যাকরণসম্মত বহুবচন। পণ্ডিতজী তার নাম বহুবচনে ব্যবহার করেন এবং আমাদেরও তাই করা উচিত। এস্থলে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে বে। ফার্সীতে আসলে শব্দটি ‘গওহর’; কিন্তু আরবী বর্ণমালায় ‘গ’ নেই বলে আরবরা জওহর’ লেখেন। পরবর্তী যুগে ‘গওহর’ ও প্রচলিত হয়। তাই মুসলমানী নাম ‘গৌহর’ ও ‘জওহর।’ একই।
নিশীথদা
কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, নিঃস্বাৰ্থ দেশসেবক শ্ৰীযুক্ত নিশীথচন্দ্ৰ সেন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদেশের বহু গুণী জ্ঞানী, বহু প্ৰখ্যাত কমী তার সংস্রবে এসেছিলেন—এমন কি একথা বললে ভুল বলা হবে না যে, দেশসেবা করেছেন, কিন্তু শ্ৰীযুক্ত নিশীথ সেনের সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি, এরকম লোক বাঙলা দেশ দেখে নি। তাই নিৰ্ভয়ে বলতে পারি, কৃতী নিশীথ সেনের কর্মজীবনের প্রশস্তি কীর্তন করার লোকের অভাব হবে না।
আমি কিন্তু নিশীথদাকে সেভাবে চিনি নি। আমি তাঁকে পেয়েছিলুম। বন্ধুরূপে, তার জীবন-অপরাহ্নে। তিনি তখন কলকাতার ভিতর-বাইরে এতই সুপরিচিত যে প্রথম আলাপের দিন কেউ আমাকে বুঝিয়ে বলল না, নিশীথ সেন বলতে কি বোঝায়। তারপর নানা রকম গাল-গল্পের মাঝখানে কে যেন আমাকে বললে, ‘আনন্দবাজারে যে ইংরেজকে একটু-কাঁটব্য আরম্ভ করেছ (আমি তখন সত্যপীর’ নাম নিয়ে ঐ কাগজে কলমে ধার দিচ্ছি) তার আগে খবর নিয়েছ কি, সিডিশন, ডিফেমশন, মহারাণীর বিরুদ্ধে লড়াই, এসব জিনিসের অর্থ কি?’ আমি কোনো কিছু বলবার আগেই নিশীথ সেন বললেন, ‘আমরাই জানি না, উনি জানবেন কি করে? আপনি তো দর্শনে ডক্টর, না? আমি সবিনয়ে বললুম, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’ নিশীথ সেন আমার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, ইংরেজ তার সমালোচককে জেলে ঠেলবার জন্য যেসব আইনকানুন বানিয়েছে, সেগুলো কোন স্থলে প্ৰযোজ্য, কাকে সেই ডাণ্ডা দিয়ে ঠ্যাঙানো যায়, তার টীকাটিপ্লনী, নজীর-দলিল। ইংরেজ আপন হাতেই রেখেছে। সুবিধেমত কখনো সেটা টেনে টেনে রবারের মত লম্বা করে, কখনো ফাঁদ ঢিলে করে পাখিকে উড়ে যেতেও দেয়। এ দেখুন না, লোকমান্য টিলককে যে আইনের জোরে জেলে পুরল, সে আইন ওরকম ধারা কাজে লাগানো যায়। সে কথা একেবারে আনাড়ি উকিলও মানবে না। তবু টিলককে তো জেলে যেতে হল। তাই সিডিশন কিসে হয়। আর কিসে হয় না, সেকথা ঝানু উকিলরা পর্যন্ত আগেভাগে বলতে পারে না। ইংরেজ যদি মনস্থির করে আপনাকে আলিপুর পাঠাবে। তবে সে তখন আপনার বিরুদ্ধে অনেক নূতন-পুরাতন আইন বের করবে। আমরা—অর্থাৎ উকিল ব্যারিস্টাররা-তখন তার বিরুদ্ধে লড়ি, সব সময়ে যে হারি তাও বলতে পারি নে।’ তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ‘আমার ফোন নম্বরটা জানেন তা? কোনো অসুবিধে হলে ফোন করবেন! আমি যা পারি করে দেব।’
প্যারীদা কান পেতে শুনছিল, লক্ষ্য করি নি। তক্ষুনি বললে, নম্বরটা টুকে নাও, ওহে আলী। কাজে লাগবে।’
পরে খবর নিয়ে জানতে পারলুম, নিশীথদা কত বড় ডাকসাইটে ব্যারিস্টার এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেই আলিপুরের আলম থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচজনের জানা অজানাতে কত অসংখ্যবার ফীজ না নিয়ে বিপ্লবীদের জন্য লড়েছেন। লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠলো।
কিন্তু থাক এসব কথা। পূর্বে নিবেদন করেছি, এসব কথা গুছিয়ে বলবার জন্য লোকের অভাব হবে না।
নিশীথদা প্ৰায় আমার বাপের বয়সী ছিলেন, কিন্তু কি করে তিনি যে একদিন দাদা হয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, তাকে ‘তুমি’ বলতে আরম্ভ করে দিয়েছিসে শুধু যাঁরা নিশীথদাকে চিনতেন তাঁরাই বলতে পারবেন।
একই প্লেনে শিলং গেলুম, সেখানে প্যারীদার বাড়িতে উঠলুম। সিগার ফুকতে ফুকতে আমার ঘরে ঢুকে খাটের একপাশে বসে বললেন, ‘কবি (বিশ্বসাক্ষী, আমি কবি নই), চমৎকার ওয়েদার, বাইরে এসো।’ বাইরে মুখোমুখি হয়ে বসলুম, তিনি নানা রকমের প্রাচীন কাহিনী বলে যেতে লাগলেন; অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন বাঁড়ুয্যে, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখুজ্যে, আব্দুর রসুল এঁদের সম্বন্ধে এমন সব কথা বললেন, যার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, কতখানি পাণ্ডিত্য, কত গভীর অন্তদৃষ্টি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকলে পরে মানুষ এত সহজে বাঙলা দেশের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এবং তার কৃতী সন্তানদের জীবনী একবার মাত্র না ভেবে অনর্গল বলে যেতে পারে। আজ আমার দুঃখের অবধি নেই, কেন সেসব কথা তখন টুকে রাখলুম না।
আমি মুর্খের মত মাঝে মাঝে আপত্তি উত্থাপন করেছি এবং খাজা গবেটের মত আইন নিয়েও। নিশীথদার চোখ তখন কৌতুক আর মৃদুহাস্যে জ্বলজ্বল করে উঠত। চুপ করে বাধা না দিয়ে শুনতেন। তারপর মাত্র একদিন চোখা যুক্তি দিয়ে আমাকে দুটুকরো করে কেটে ফেলতেন। আমার তাতে বিন্দুমাত্র উত্তাপ বোধ হয় নি। তাই শেষের দিকে যখন যে সব জিনিস নিয়ে আমি মনে মনে দম্ভ পোষণ করি, এই লোকটির সংস্রবে। আসতে পেরেছি বলে।
কী অমায়িক অজাতশত্রু পুরুষ! আর কী একখানা মেহকাতর হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। আইন আদালতের খররৌদ্র তার সে শ্যামমনোহর হৃদয়ে সামান্যতম বাণ হানতে পারে নি।
তার বয়স তখন সত্তর। সেই শিলঙে একদিন সকাল বেলা দেখি, ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত পুরে বারান্দায় ঘন ঘন পইচারি করছেন, মুখে সিগার নেই। কথা কয়ে ভালো করে উত্তর পাইনে। কি হয়েছে, ব্যাপার কি নিশীথদা?
তিন দিন ধরে স্ত্রীর চিঠি পান নি।
সে কি নিশীথদা, সত্তর বছর বয়সে এতখানি?
সেই জ্বলজ্বলে চোখ-সে চোখ দুটি কেউ কখনো ভুলতে পারে।–দিয়ে বললেন, ‘কবি, সব জানো, সব বোঝে, কিন্তু বিয়ে তো করো নি, তাহলে এটাও বুঝতে।’
নিশীথদা, বউদিকে বড্ড ভালোবাসতেন। আমি জানি নিশীথদা আরো কিছুদিন কেন এ সংসার থাকলেন না।
ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ডসৌভাগ্যবতী শ্ৰীমতী শোভনা ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশীথদার জীবনের জ্যোতি যেন নিভে গিয়েছিল।
আজ বোধ হয় নিশীথদার আর কোন দুঃখ নেই–আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।
ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।
নেভার রাধা
অনেক প্রেমের কাহিনী পড়েছি, এমন সব দেশে বহু বৎসর কাটিয়েছি যেখানে প্রেমে না। পড়াতেই ব্যত্যয়—তাই চোখের সামনে দেখেছি প্রেমের নিত্য নব প্যাটার্ন-কিন্তু একটা গল্প আমি কিছুতেই ভুলতে পারি নে। তার প্রধান কারণ বোধ হয়। এই যে গল্পটি বলেছেন ওস্তাদ তুৰ্গেনিয়েফ। এবং শুধু তাই নয়-ঘটনাটি তার নিজের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছিল।
দস্তয়েফস্কি, তলস্তয়ের সৃজনীশক্তি তুৰ্গেনিয়েফের চেয়ে অনেক উঁচুদরের, কিন্তু তুৰ্গেনিয়েফ যে স্বচ্ছসলিল ভঙ্গিতে গল্প বলতে পারতেন, সেরকম কৃতিত্ব বিশ্বসাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন অতি অল্প ওস্তাদাই! তুৰ্গেনিয়েফের শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক রুশ সমঝদার বলেছেন, ‘তাঁর শৈলী যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে-ইট ফ্লোজ লাইক অয়েল।’
তুৰ্গেনিয়েফ ছিলেন খানদানী ঘরের ছেলে-তলস্তয়েরই মত। ওরকম সুপুরুষও নাকি মস্কো, পিটার্সবুর্গে কম জন্মেছেন। কৈশোরে তাঁর একবার শক্ত অসুখ হয়। সেরে ওঠবার পর ডাক্তার তাঁকে হুকুম দেন নেভা নদীর পারে কোনো জায়গায় গিয়ে কিছুদিন নির্জনে থাকতে। নেভার পারে এক জেলেদের গ্রামে তুৰ্গেনিয়েফ পরিবারের জমিদারি ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে জমিদারের একখানি ছোট্ট বাঙলো-চাকর-বাকর নিয়ে ছোকরা তুৰ্গেনিয়েফ বাঙলোয় গিয়ে উঠলেন।
সেই ছবিটি আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জমিদারের ছেলে, চেহারাটি চমৎকার আর অসুখ থেকে উঠে সে চেহারাটি দেখাচ্ছে করুণ, উদাস-উদাস, বেদনাতুর। তার উপর তুৰ্গেনিয়েফ ছিলেন মুখচোরা এবং লাজুক, আচরণে অতিশয় ভদ্র এবং নম্র। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, গ্রামে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছে—জেলে-মেয়েরা দূর থেকে আড়নয়নে দেখছে তুর্গনিয়েফ মাথা নিচু করে, দুহাত পিছনে একজোড় করে নদীর পারে পইচারি করছেন। জরাজীর্ণ গ্রামে হঠাৎ যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।
মেয়েরা জানে এরকম খানদানী ঘরের ছেলে তাদের কারো দিকে ফিরেও তাকবে না, কিন্তু তা হলে কি হয়, তরুণ হৃদয় অসম্ভব বলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে না। সে রবিবারে জেলে-তরুণীরা গির্জয় গেল দুরুদুরু বুক নিয়ে—বড়দিনের ফ্রক-ব্লাউজ পরে।
তরুণীদের হৃদয় ভুল বলে নি। অসম্ভব সম্ভব হল। তুৰ্গেনিয়েফ মেয়েদের দিকে তাকালেন। তার মনও চঞ্চল হল।
তুৰ্গেনিয়েফ পক্টাপষ্টি বলেন নি, কিন্তু আমার মনে হয় মস্কো পিটার্সবুর্গের রঙমাখানো গয়না-চাপানো লোক-দেখানো সুন্দরীদের নখরা-ককেস্ট্ররি তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছিল বলে তিনি জেলে-গ্রামের অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্যের সামনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তুর্গেনিয়েফের কবিহৃদয় অতি সহজেউ হীরা ফুল অনাদর করে বুনো ফুল আপন বুকে গুঁজে নিয়েছিল।
কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের সুন্দরীদের পয়লানম্বরি কাউকে তিনি বেছে নিলেন না। এই উল্টো স্বয়ম্বরে যাকে তিনি হৃদয় দিলেন সে স্বপ্নেও আশা করতে পারে নি, এই প্রিয়দর্শন তরুণটি সুন্দরীদের অবহেলা করে তাকেই নেবে বেছে। সত্য বটে মেয়েটি কুৎসিত ছিল না, এবং তার স্বাস্থ্যও ছিল ভালো; কিন্তু তাই দিয়ে তো আর প্রেমের প্রহেলিকার সমাধান হয় না ।
মেয়েটির মনে যে কী আনন্দ, কী গর্ব হয়েছিল সেটা কল্পনা করতে আমার বড় ভালো লাগে। তুৰ্গেনিয়েফ তার অতি সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা দিয়েছেন-নিজের জীবনে ঘটেছিল। বলে হয়ত তিনি এ ঘটনাটিকে বিনা অলঙ্কারে বর্ণনা করেছেন। আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছে হয়, মেয়েটির লজ্জা-মেশানো গর্ব যদি আরো ভালো করে জানতে পারতুম—তুৰ্গেনিয়েফ যদি আরো একটুখানি ভালো করে তার হৃদয়ের খবরটি আমাদের দিতেন।
শুধু এইটুকু জানি মেয়েটি দেমাক করে নি। ইভানকে পেয়ে সে যে-লোকে উঠে গিয়েছিল সেখানে তো দেমাক দম্ভের কথাই উঠতে পারে না। আর তুৰ্গেনিয়েফ হিংসা, ঈর্ষা থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অন্য মেয়েদের সঙ্গে অতি ভদ্র মিষ্টি আচরণ দিয়ে–কোনো জমিদারের ছেলে নাকি ওরকমধারা মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিচু হয়ে জেলেনীদের কখনো নমস্কার করেনি।
কৈশোরের সেই অনাবিল প্রেম কিরূপে আস্তে আস্তে তার বিকাশ পেয়েছিল, তুৰ্গেনিয়েফা তার সবিস্তার বর্ণনা দেন নি।–তাই নিয়ে আমার শোকের অন্ত নেই।
দুজনে দেখা হত। হাতে হাত রেখে তারা নদীর ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদ উঠত। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে তুৰ্গেনিয়েফ তার ওভারকেট দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে দিতেন। সে হয়ত মৃদু আপত্তি করত—কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ইভানের কোনো ইচ্ছায় সে বেশিক্ষণ বাধা দিতে পারত না।
তুৰ্গেনিয়েফ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। বাড়ি থেকে হুকুম এসেছে প্যারিস যেতে।
বিদায়ের শেষ সন্ধ্যা এল। কাজ সেরে মেয়েটি যখন ছুটে এল ইভানের কাছ থেকে বিদায় নিতে, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।
অঝোরে নীরবে কেঁদেছিল। শুধু মেয়েটি। তুৰ্গেনিয়েফ বারে বারে সাত্বনা দিয়ে বলেছিলেন ‘তুমি এরকম ধারা কাঁদিছো কেন? আমি তো আবার ফিরে আসব-শিগগিরই। তোমার কান্না দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাবছি, আমি আর কখনও ফিরে আসব না।’
কিন্তু হায়, এসব কথায় কি ভাঙা বুক সান্ত্বনা মানে? জানি, তুৰ্গেনিয়েফের তখনো বিশ্বাস ছিল তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু যে ভালোবসেছে সমস্ত সত্তা সর্বৈব অস্তিত্ব দিয়ে তার হৃদয় তো তখন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়-বিধাতা পুরুষেরই মত।
তুৰ্গেনিয়েফ বললেন, ‘তোমার জন্য প্যারিস থেকে কি নিয়ে আসব?’
কোনো উত্তর নেই।
‘বল কি নিয়ে আসব?’
‘কিচ্ছু না–শুধু তুমি ফিরে এসো।’
কিছু না? সে কি কথা? আর সবাই তো এটা, ওটা, সেটা চেয়েছে। এই দেখো, আমি নোটবুকে সব কিছু টুকে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে দামী জিনিস আনতে চাই। বলো কি আনব?’
‘কিচ্ছু না।’
তুৰ্গেনিয়োফকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল, মেয়েটির কাছ থেকে কোন একটা কিছু একটার ফরমাইশ বের করতে। শেষটায় সে বললে, ‘তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান নিয়ে এসো।’
তুৰ্গেনিয়েফ তো অবাক। এই সামান্য জিনিস! কিন্তু কেন বলে তো, তোমার আজ সাবানে শখ গেল? কই তুমি তো কখনো পাউডার সাবানের জন্য এতটুকু মায়া দেখাও নি—তুমি তো সাজগোজ করতে পছন্দ কর না।’
নিরুত্তর।
‘বলো।‘
‘তা হলে আনবার দরকার নেই।’ তারপর ইভানের কেলৈ মাথা রেখে কেঁদে বলল, ‘ওগো, শুধু তুমি ফিরে এসো।’
‘আমি নিশ্চয়ই সাবান নিয়ে আসব। কিন্তু বল, তুমি কেন সুগন্ধি সাবান চাইলে?’
কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বলল, ‘তুমি আমার হাতে চুমো খেতে ভালোবাসো আমি জানি। আর আমার হাতে লেগে থাকে সব সময় মাছের আঁশটে গন্ধ। কিছুতেই ছাড়াতে পারি নে। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনেছি সব গন্ধ কেটে যায়। তখন চুমো খেতে তোমার গন্ধ লাগবে না।’
অদৃষ্ট তুৰ্গেনিয়োফকে সে গ্রামে ফেরবার অনুমতি দেন নি।
সে দুঃখ তুৰ্গেনিয়েফও বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি।
নয়রাট
দেশভ্রমণের সময় যারা ছন্নের মতো ছুটোছুটি করে-অর্থাৎ সকালে মিউজিয়াম, দুপুরে চিত্রশালা, বিকেলে গির্জে দর্শন, সন্ধ্যায় অপেরা, রাতদুপুরে কাবারে, আমি তাদের দলে নেই। দেশে ফেরার পর কোনো পাক্কা টুরিস্ট যদি আশ্চর্য হয়ে বলেন, ‘সে কি হে? তুমি প্রাগে তিন দিন কাটালে। অথচ বলছি। রাজা কালের বর্মাভিরণ-অস্ত্রশস্ত্রের মিউজিয়াম দেখ নি-এ তো অবিশ্বাস্য’, আমি তাহলে তা নিয়ে তর্কাতর্কি করিনে কারণ মনে মনে জানি আমি প্রত্যেকটি কড়ির পুরো দাম তোলার জন্য দেশভ্রমণে বেরই নি। ছ। পয়সার টিকিট আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত নিয়ে যায়-আমি নামিব হেদোয়-তাই আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত গিয়ে সেখানে নেমে, পায়ে হেঁটে ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে হেদোয় এসে বেঞ্চিতে বসে ধুঁকতে হবে নাকি? আটনম্বরের জুতো ছটাকায় দিচ্ছে বলে আমার ছ নম্বরী পা-কে আট-নম্বরী পরাতে যাব নাকি?
তাই আমার উপদেশ ও কর্মটি করতে যাবেন না। খাওয়ার যেরকম সীমা আছে, ভালো জিনিস দেখারও একটা সীমা আছে। ক্লান্তি বোধ হলেই দেখা ক্ষান্ত দিয়ে একটা কাফেতে বসে যাবেন কিংবা যদি বাগানে বসবার মতো আবহাওয়া হয় তবে বাগানে বসে কফি, চা, বিয়ার কিছু একটা অর্ডার দিয়ে সিগারেটটি ধরিয়ে আরামসে গা এলিয়ে দেবেন।
এই হল জাবর-কাটার মোকা। এ কদিনে যা কিছু দেখেছেন তার মধ্যে যে কটি মনে ঢেউ তুলেছিল। সেই ঢেউগুলি শুনবেন। কিংবা বলব আপনার মনের ফিল্ম যে ছবিগুলো তুলেছিল তার গুটিকয়েক ডিভলাপ প্রিনটিং করবেন, চোখ বন্ধ করে এক-একটা দেখবেন
আমার পাশের টেবিলে দুই পাঁড় দাবাখেলনেওলা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে দাবা খেলছিলেন। দু’কাপ কফি হিম হয়ে গিয়েছে—উপরে কফির ঘন সর পড়েছে। জামবাটি সাইজ অ্যাশ-ট্রে পোড়া সিগারেটে ভর্তি। আরো জনতিনেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, কিন্তু কারো মুখে কথা নেই, এ দৃশ্য বাঙালিকে রঙ ফলিয়ে দেখাতে হবে না। কৈলাস খুড়োর যে ছবি শরচ্চন্দ্র এঁকে গিয়েছেন তার দোহার গাইবার প্রয়োজন বাঙলাদেশে বহুকাল ধরে হবে না।
খেলোয়াড়দের একজন দেখলুম ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে আসছেন। আধা ঘণ্টাতেই কাবু হয়ে গেলেন। গজের কিস্তিতে যখন মাত হবু-হবু, তখন ঘাড়গির্দানে ‘শ্রাগ’ করে। বললেন, ‘স্পাঞ্জ ফেলে দিলুম, অর্থাৎ আমার খেলা গয়াগঙ্গাগদাধরহরি।
দর্শকদের একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, ‘কেন? ঐ বড়েটা একঘর ঠেলে দিলে হয় না?’
খাসা চাল তো! ওদিকে কারো নজরই যায় নি। এ চালে আরো খানিকক্ষণ লড়াই দেওয়া যেতে পারে।
খেলোয়াড়টি উঠে দাঁড়িয়ে সেই দর্শককে বললেন, ‘আপনি তাহলে বসেন।’ দর্শক তখন খেলোয়াড়রূপে বসে প্রথম সামলালেন। আপনি ঘর, তার পর দিতে আরম্ভ করলেন। ধীরে ধীরে চাপ। স্পষ্ট বোঝা গেল ইনি উচ্চাঙ্গের লেঠেল। এবার অন্য পক্ষের প্রাণ যায় আর কি। শেষটায়। তাই হল। পয়লা বারের কসাই এবারে বকরি হয়ে বললেন-যা বললেন-তার অর্থ ‘হরিবোল বল হরি!’
আমরা লক্ষ্য করি নি কেইবা এরূপ স্থলে করে-আরো জনতিনেক দর্শক তখন বেড়ে গিয়েছেন। তাঁদেরই একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, ‘কেন, গজটা পেছিয়ে নিলে হয় না?’
এ চালের অর্থটা আমার কাছে ধরা পড়ল না। কিন্তু কসাই দেখলুম ধরতে পেরেছেন। শুধু বললেন, ‘হুঁ।’ তখন পয়লা বারের কসাই, দুসর বারের বকরি উঠে বললেন, ‘আপনি তা হলে বসুন।’
অর্থাৎ খোল-নীলচে দুইই তখন বদলে গিয়েছে।
এবারে সত্যি সত্যি লাগল মোষের লড়াই।
শেষটায় খেলা চাল-মাত হল।
***
ফিরে এসে আপন চেয়ারে বসলুম।
খেলোয়াড়দের একজন তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক চণ্ডু-খানায় যখন এতক্ষণ একসঙ্গে আফিং খেয়েছি তখন খানিকটে পরিচয় হয়ে গিয়েছে বই কি-একটা ছোট নড় করলুম। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন, ‘সুপ্ৰভাত।’ আমি বললুম, ‘বসুন, বসুন!’
ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, ‘‘বসুন’, হুঁঃ, ‘বসুন’’। ওদিকে আমার প্রাণ যায় আর কি?’
আমি শুধালুম, ‘কেন, কি হয়েছে?’ বুঝলুম লোকটি দিলখোলা।
বললেন, ‘জবাই করবে, মশাই, জবাই করবে। আমাকে-বউ। বলেছিলুম, এই এলুম। বলে। কি করে জানব বলুন, দাবার চক্করে পড়ে যাব। বলতে পারেন, মশাই, এই বিদঘুটে খেলা বের করেছিল কে? হাঁ, হাঁ, ভারতবর্ষেই তো এর জন্মভূমি। কিন্তু এদেশে এল কি করে?’
‘শুনেছি পারসিকরা আমাদের কাছ থেকে শেখে, আরবরা তাদের কাছ থেকে, তারপর ক্রুসেডের লড়াইয়ে বন্দী ইয়োরোপীয়রা শেখে আরবদের কাছ থেকে, তারা দেশে ফিরে-’
‘আমাদের মজালে। কিন্তু এখন আমার উপায় কি? আপনারা এ অবস্থায় দেশে কি করেন?’
‘চাঁদ-পানা মুখ করে গাল সই।’
‘ব্যস! ব্যামোটা বাধিয়ে বসে আছেন ঠিক; ওষুধটা বের করতে পারেন নি। কিন্তু আমি পেরেছি। চলুন, আমার সঙ্গে, লঞ্চ খাবেন।’
‘আর গালও খাব? না?’
‘না, না, আপনাকে বকিবে কেন? আমি বলব, এর সঙ্গে গল্প করতে করতে কি করে যে বেলা বয়ে গেল ঠাহর করতে পারি নি। চলুন, চলুন আর দেরি করা নয়।’
চললুম।
ভদ্রলোকের বয়স-এই ধরুন ৪৫-৪৬। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, পরনে উত্তম রুচির কোটপাতলুন-টাই। সব কিছু পরিপাটি। তাই অনুমান করলুম। তাঁর অর্ধাঙ্গিনী তাকে বকুন-ঝকুন আর যা-ই করুন না কেন, গৃহিণী হিসেবে তিনি ভালোই।
বললেন, ‘যা খুশি তাই বউকে বলে যাবেন, কিছু ভয় করবেন না। তাকে যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বানিয়ে সিংহলে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাতেও আমি কোনো আপত্তি করব না, কিন্তু স্যার, দয়া করে ঐ দাবা খেলার কথাটি চেপে যাবেন।’
আমি বললুম, ‘নিশ্চয়ই।’
দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং স্ত্রী। কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার পূর্বেই ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিলেন, ‘ইনি আমার স্ত্রী, ফ্রানৎসিসকো-ফ্রানৎসিস্কা নয়রাষ্ট্ৰ।’ আমি বললুম, ‘আমার নাম আলী।’
ফ্রানৎসিস্কার বয়স ৩৫-৩৬ হবে। সুইজারল্যান্ডে এই বয়সে মেয়েদের পূর্ণ যুবতী বলে ধরা হয়। এ-যৌবনে কুমারীর রূপের নেশা আর মাতৃত্বের মাধুরী মিশে গিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তার রস মানুষ নিৰ্ভয়ে উপভোগ করতে পারে—স্বামী সন্দেহের চোখে দেখে না, রমণী আপনার চোখে চটক লাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। মেয়েদের আচরণ এ সময় সত্যই বড় মধুর হয়; কখনো তারা তরুণীর মতো ভাবে বিহ্বল আত্মহারা হয়ে অকারণ বেদনার কাহিনী বলে যায়, কখনো আবার মাতৃত্বের গর্ব নিয়ে আপনাকে নানা সদুপদেশ দেয়, বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার পাতবার জন্য স্নিগ্ধচোখে অনুনয়-বিনয় করে।
স্ত্রীকে কিছু বলতে না দিয়েই হ্যার নয়রাটু বকে যেতে লাগলেন, ‘বুঝলে ফ্রানৎসিস্কা, আমি ঠিক সময়েই ফিরে আসতুমি কিন্তু এই হার আলীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ইনি ভারতবর্ষের লোক-শুনেছি তো ভারতবর্ষের লোক কি রকম গুণী-জ্ঞানী হয়। ইনি তাঁদেরই একজন। তার প্রমাণও আমি হাতে-নোতে পেয়ে গিয়েছি। রাস্তায় আসতে আসতে তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেলুম, সাতদিন ধরে এসেছেন জিনীভায়, এখনো লীগ অব নেশনসের ‘চিড়িয়াখানা’ দেখতে যান নি, শামুনিক্স চড়েন নি, অপেরা থিয়েটার কিছুই দেখেন নি। আর সব টুরিস্টদের মতো সুইটজারল্যান্ডের প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বস্তুকে পিঁপড়ে নিঙড়ে ঘি বের করাবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন নি। আমার তো মনে হয়, এ-দেশের উচিত এঁকে এঁর খর্চর পয়সা কিছু ফেরৎ দেওয়া। কী বল?’
পাছে ভদ্রমহিলার অভিমানে ঘা লাগে, আমি তার দেশের কুতুব তাজ ভারতীয় দম্ভের নেশায় তাচ্ছিল্য করছি তাই তাড়াতাড়ি বললুম, ‘আমি বড় দুর্বল, বেশি ঘোরাঘুরি করলে ক্লাস্ত হয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে সব-কিছুই দেখে নেব।’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘সেই ভালো। শামুনিরুক্স পাহাড় তো আর বসন্তের বরফ নয় যে দুদিনে গলে যাবে, সুইটজারল্যান্ড ভ্ৰমণ তো আর দাবাখেলা নয় যে সুযোগ পেয়েও দুটি কিস্তি না দিলে—’
বাকিটা আমি আর শুনতে পাইনি। আমি তখন ওয়াল-পেপার হয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যাবার জন্য আস্তে আস্তে পিছুপা হতে আরম্ভ করেছি।
শুনি, হ্যার নয়রাটু ব্যথা-ভরা সুরে বলছেন, ‘গিন্নি, ছিঃ।’
আমার অবস্থা তখন এক মাতাল আরেক স্যাঙাত মাতালকে সাফাই গাইবার জন্য নিয়ে এসে ধরা পড়লে যা হয়।
নাঃ, ভুল করেছি। ফ্রানৎসিস্কার কামড়ানোর চেয়ে ঘেউ-ঘেউটাই বেশি। বললে, ‘আঃ, আপনারাও যেমন। মেয়েছেলে এরকম দু-একটা কথা সব সময়েই কয়ে থাকেনওসব কি গায়ে মাখতে আছে? তুমি দাবা-খেলায় দু-একটা আজেবাজে চাল মাঝে মাঝে দাও না-দুশমন কি করে তাই দেখবার জন্য?’
আবার দাবা। খেয়েছে।
ফ্রানৎসিস্কা স্বামীকে বললেন, ‘আজ তো লাঞ্চের ব্যবস্থা বড় মামুলী। সুপ ফিশ আ লা রুসে (রাশান কায়দায়) আর অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপটু ক্রম। তার চেয়ে বরঞ্চ চল রেস্তোরাঁয়-জিনীভা লেকের মাছ সুইস কায়দায় রান্না—ভালোমন্দ এটা সেটা।’ তারপর আমার দিকে তাকিয়ে শুধালেন, ‘আপনি কি খেতে ভালোবাসেন?’
আমি নিৰ্ভয়ে বললুম, ‘সুপ, ফিশ আ লা রুস, অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপটু ক্ৰীম।’
হ্যার নয়রাষ্ট্র তো আনন্দে গদগদ। বললেন, ‘দেখলে গিন্নি, কি রকম অদ্ভুত আদবকায়দা। তুমি যদি বলতে আজ রোধেছি স্ট্রিকনিন-সুপ, পটাসিয়াম সায়ানাইড-ফ্রাইড, আর্সেনিক-পুডিং আর কোবরা-রসের কফি তা হলে উনি বলতেন, ‘দি আইডিয়া, আমি দু, বেলা ঐ জিনিস খাই’।’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘দেখো, পেটার, বিশ্বসংসারের লোককে তুমি আপন মাপকাঠি দিয়ে মেপো না। তোমার মত ওঁর পেট অজুহাতের মানওয়ারী জাহাজ নয়।’
পেটার বললেন, ‘সব দাবা-খেলোয়াড়কেই অজুহাত-বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয়। বিয়ের পরেই যে রকম হনিমুন, দাবা-খেলার পরই সেই রকম অজুহাত অন্বেষণ!’
আমি বললুম, ‘কিন্তু আমি তো দাবা খেলি নে!’
কথা শুনে দুজনাই খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষটায় পেটার বললেন, ‘দেখলে গিন্নি, অজুহাতের রাজা করে কয়? একদম কবুল জবাব উনি দাবা খেলেন না! বাপস! মারি তো হাতি লুটি তো ভাণ্ডার। অজুহাত যদি দিতেই হয় তবে এমন একখানা ঝাড়ব যে মানুষ রা কাড়বার ফাঁকটি পাবে না। পাক্কা আড়াই ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখলেন আমাদের খেলা, আর এখন অস্নান বদনে বলছেন। উনি দাবা খেলেন না!’
আমি সবিনয়ে শুধালাম, ‘আপনি কনসার্ট শুনতে যান? আচ্ছা, সেখানে তো পাকি সাড়ে তিন ঘণ্টা বাজনা শোনেন; তাই বলে কি আপনি পিয়ানো, ব্যালা, চেল্লো কত্তাল বাজান?’
ওদিকে দেখি ফ্রানৎসিস্কা আমাদের তর্কাতর্কিতে কান দিচ্ছেন না; শুধু বললেন, ‘তাই বলো, দাবা খেলা হচ্ছিল।’
চাণক্য বান্ধবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজস্বারে যে সঙ্গ দেয় সে বান্ধব। আমার বিশ্বাস চাণক্য কখনো বিয়ে করেন নি। তা না হলে তিনি ‘রাজদ্বারে’ না বলে জায়াদ্ধারে’ বলতেন।
জানি, অতিশয় অভদ্রতা হল—তবু বললুম, ‘আমার ক্ষিদে পেয়েছে।’
বন্ধুর ফাসিটাকে মুলতুবী করাতে পারলুম—এই বা কি কম সান্ত্বনা।
***
আমরা বাড়িতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে যেরকম হাপুসহুপুস শব্দ করে আহারাদি
সমাপন করি, নেমন্তন্ন খেতে গিয়েও প্রায় সেই রকমই করে থাকি। তফাত মাত্র এইটুকু যে, বাড়িতে চিৎকার করে বলি, ‘আরো দুখানা মাছভাজা দাও’, নেমন্তন্ন বাড়িতে বলি, ‘চৌধুরী মশাইকে আরো দুখানা মাছভাজা দাও।’
সায়েব-সুবোদের কিন্তু বাড়ির খাওয়াতে, রেস্তোরাঁয় আহারে এবং নেমন্তন্নের ভোজনে ভিন্ন ভিন্ন কায়দা-কেতায় খাওয়া-দাওয়া করতে হয়। সায়েবরা বাড়িতে খেতে বসে গোগ্রাসে গোস্ত গেলে আর পোশাকী ডিনারে কিংবা ব্যানকুয়েটে একরকম না খেয়েই বাড়ি ফেরে। ব্যানকুয়েটে আপনাকে সুপ দেওয়া হবে আড়াই চামচ, তার থেকে আপনি খাবেন। দেড় চামচ। ডিনারে সুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে মোলায়েম কায়দায় ঠোঁট ব্লট করবেন, কিন্তু ডুক অব উইন্ডসরের সঙ্গে ব্যানকুয়েট খেতে বসলে ঠোঁট ব্লট করাও নিষিদ্ধ, অর্থাৎ তখন ধরে নেওয়া হয়, আপনি এতই কম সুপ খেয়েছেন যে, আপনার ঠোঁট পর্যন্ত ভেজে নি। তারপর পদের পর পদ উত্তম খাদ্য আসবে-আপনি আপন প্লেটে তুলে নেবেন কখনো আড়াই আউন্স, কখনো দু আউন্স এবং খাবেন তার থেকে এক আউন্স কিংবা তার চেয়েও কম। মুর্গীর হাডি থেকে যে ছুরি দিয়ে মাংস চাচবেন তার উপায় নেই এবং গ্ৰেভিটুকুর মোহ করেছেন কি মরেছেন। সাইড প্লেটে যে এক স্নাইস টেস্ট দিয়েছিল তার একদশমাংসের বেশি খেলে পাঁচজনে ভাববে, আপনি রায়লসীমার দুৰ্ভিক্ষ-প্ৰপীড়িত ‘পারিয়া’ কিংবা মধ্য-আফ্রিকার মিশনারি-খেকো হটেনটট্।
বিশ্বাস করবেন না, এক খানদানী ক্লাবে আমি দুই পক্ষকে পাকি দু ঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি করতে শুনলুম, সসেজ কি করে খেতে হয়। সমস্যাটা এইরূপ:—(ক) সসেজ থেকে ছুরি দিয়ে চাক্তি কেটে নিয়ে তার উপর মাস্টার্ড মাখাবে কিংবা (খ) প্রথম সসেজের ডগায় মাস্টার্ড মাখিয়ে নিয়ে পরে সসেজ থেকে চাক্তি কেটে তুলবে? আমি প্রথম পক্ষের হয়ে লড়াই করেছিলুম এবং শেষটায় আমরা ভোটে হেরে গেলুম। এর থেকেই বুঝতে পারছেন, আমি খানদানী খানা খেতে শিখি নি-ব্যানকুয়েটে আমার নাভিশ্বাস ওঠে।
বিশ্বাস করবেন না, মাসখানেক হল এক সুইস খবরের কাগজে দেখি, এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন, প্লেটে যে গ্ৰেভি পড়ে থাকে, তার উপর রুটি টুকরো টুকরো করে ফেলে সেই গ্রেভি চেটেপুটে নেওয়া (জর্মন শব্দ tunken) ব্যাকরণসম্মত-অৰ্থাৎ কায়দাদুরস্ত-কি না?
উত্তরে এক ‘খানদানী মনিষ্যি’ বলেছেন, কিছুকাল পূর্বেও এ-অভ্যাস কি বাড়িতে, কি রেস্তোরাঁয়, কি ব্যানকুয়েটে সর্বত্রই অতিশয় নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হত, কিন্তু আজকের বিশ্বময় খাদ্যাভাবের দিনে বাড়িতে-আপনি ডাইনিং রুমে কর্মটি ক্ষমার্হ।
মুর্গীর ঠ্যাংটি হাতে তুলে নিয়ে কড়কড়ায়তে, মড়মড়ায়াতে’ বাড়িতে বেশির ভাগ ইউরোপীয়ই করে, কিন্তু বাইরে নৈব নৈব চ। তবে কোন কোন জর্মন এবং সুইস রেস্তোরাঁয় রোস্ট সার্ভ করবার সময় মুর্গীর ঠ্যাংগুলো উপরের দিকে সাজিয়ে রাখে এবং ঠ্যাংগুলোর ডগায় বাটার পেপারের ক্যাপ পরিয়ে দেয়, যাতে করে আপনি হাত নোংরা না করে ঠ্যাংটা চিবুতে পারেন। এ ব্যবস্থা দেখে ইংরেজের জিভে জল আসে, কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বলে, ‘জার্মানরা বর্বর!’
অপিচ এসপেরেগাস এবং আর্টিচোক ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়া গো-হত্যার ন্যায় মহাপাপ–খেতে হয় হাত দিয়ে।
ইংরেজ যদিস্যাৎ কখনো রাইস-কারি কিংবা ইটালিয়ান রিসোট্রো (এক রকমের কিমাপোলাও) খায়, তবে টেবিল কিংবা ডেসার্ট স্পপুনি দিয়ে সে খাদ্য মুখে তোলে। তাই দেখে ফরাসি-ইতালি আঁতকে ওঠে—বলে, কী বর্বরতা! একটা আস্ত চামচ মুখে পুরছে।-বাপস। তারা রাইস-কারি খায় ডান হাতে কাঁটা নেয়—বিনা ছুরিতে। তাই দেখে চীনা ভদ্রসন্তান আবার ভিরমি যায়। বলে, একটা আস্ত ফর্ক মুখে ঢোকাচ্ছে-কী বর্বরতা! তার চেয়ে চপস্টিক কত পরিষ্কার, কত পরিপাটি।
আর বঙ্গসন্তান আমি বলি, এ সবকটি পদ্ধতিই বর্বর না হোক, অন্তত নোংরা। ফর্ক, স্পপুনি, এমন কি চপস্টিক পর্যন্ত আমার আপনি আঙুলের চেয়ে নোংরা। সব চেয়ে বটীয়া হোটেলের স্পপুনি নিয়ে আপনি আচ্ছাসে ন্যাপকিন দিয়ে ঘষুন-দেখতে পাবেন ন্যাপকিন কালো হয়ে গেল। অথচ আপনি হাত ধুয়ে যে খেতে বসেন, তখন কাপড়ে আঙুল ঘষলে কাপড় ময়লা হয় না।
কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি টেবিলে বসে খাওয়াতে। টেবিল ক্লথ বাঁচিয়ে, ছুরি-কাঁটা না বাজিয়ে, জল খাওয়ার সময় গ্লাসে ঠোঁটের দাগ না লাগিয়ে টেবিলের তলায় পাশের কিংবা আসনের লোকের পায়ে গুস্তা না মেরে আপন গেলাস আর পরের গেলাসে খিচুড়ি না পাকিয়ে, আঁত্রের ফর্ক আর জয়েন্টের ফর্কে গোলমাল না বাধিয়ে, প্লেট শেষ হওয়ার পূর্বে ছুরি-কাঁটা পাশাপাশি না রেখে, ডাইনে-বঁয়ে সব কিছু রদিবরবাদ না করে, এবং আহারান্তে ঘোত ঘোত করে ঢেকুর না তুলে আহার করা আমার পক্ষে কঠিন, সুকঠিন। বিলিতি ডিনার খেতে পারেন মাত্র ম্যাজিশিয়ানরাই যাঁদের হাত-সাফাই আছে, যাঁরা চিড়িতনের টেক্কাকে বেমালুম হরতনের নয়লা বানিয়ে দিতে পারেন।
এবং সব চেয়ে গর্ভ-যন্ত্রণা, খাওয়ার দিকে আপনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন। না। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে আপনাকে মধুর মধুর বাক্যালাপ করতে হবে। আবহাওয়া থেকে আরম্ভ করে আপনাকে রিলেটিভিটি পর্যন্ত কপচাতে হবে। আবার শুধু গল্প করলে চলবে না—সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে। এর পরিমাণ সঠিক রাখা সেও এক কঠিন কর্ম। আপনি যদি প্রধান অতিথি হন, তবে আপনাকে বকর বকর করতে হবে বেশি, যদি আমার মতো ব্যাকবেঞ্চার হন, তবে চুপ করে সব কিছু শুনে যেতে হবে-তা সে যতই নিরস নিরানন্দ হোক না কেন?
বলুন তো মশাই, ভোজনের নেমন্তন্ন কি এগজামিনেশন হল?
***
নয়রাট লোকটি খুশ গল্প করে ঘরবাড়ি জমজমাট করে রাখতে চান সে কথাটা দু মিনিটেই বুঝে গেলুম, আর গৃহিণীর ভাবসাব দেখে অনুমান করলুম। ইনিও সাদাসিধে লোক, লৌকিকতার বড় ধার ধারেন না। খানাটেবিলের পাশে পৌঁছেই বললেন, ‘এ বাড়িতে পোলিশ গৰ্ভমেন্ট, (পোল্যান্ডের ইতিহাসে এত ঘন ঘন অরাজকতা আর বিদ্রোহ হয়েছে যে, জর্মন ভাষায় ‘পোলিশ গভর্নমেন্ট’ বলতে ‘এলো-মেলো’ ‘ছন্নছাড়া’ বোঝায়) যে যেখানে খুশি বসতে পারেন।’
নয়রাট বাধা দিয়ে বললেন, ‘সে কি করে হয়? আমি বসব আমার পশ্চাদেশের উপর, তুমি বসবে।–’
ফ্রানৎসিস্কা রাগ করে বললেন, ‘ছিঃ, পেটার, ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে এই আজ সকালে; আর এরই ভিতর তুমি আরম্ভ করে দিয়েছ যত সব অশ্লীল কথা! তার উপর উনি আবার বিদেশী।’
নয়রাট বললেন, ‘দেখো, প্রিয়া, তুমি অনেকগুলো ভুল করেছ। প্রথমত তুমি বিলক্ষণ জানো, আমি দিশি-বিদেশীতে কোন ফারাক দেখতে পাই নে। যার সঙ্গে আমার মনের মিল, রুচির মিল হয় সে-ই আমার আত্মজন। কি বলেন আলিসাহেব?’
আমি বললুম, ‘অতি খাঁটি কথা। তবে ভারতীয় ঋষি বলেছেন, ‘আমি’ ‘তুমি’তে পার্থক্য করে লঘুচিত্তের লোক, যার চরিত্র উদার তার কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন।
নয়রাটি গুম মেরে শুনলেন। অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়ে শেষটায় বললেন, ‘এটা হজম করতে আমার একটু সময় লাগবে—ফ্রানৎসিস্কার রান্নার মতো।’
ফ্রানৎসিস্কা ভয়ঙ্কর চটে যাওয়ার ভান করে (আমার তাই মনে হল) বললেন, ‘দেখো, পেটার, তুমি খাওয়া বন্ধ করে এখখুনি রেস্তোরাঁ যাও; না হলে এই ডিশ ছুঁড়ে তোমার মাথা ফাটাব।’
পেটার অতি ধীরে ধীরে আরেক চামচ টমাটো সুপ গিলে নিয়ে প্রথম গিন্নিকে শুধালেন, আরো সুপ আছে কি না, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘সবাইকে আত্মজ করা কি কখনো সম্ভব? এই দেখুন না, সেদিন ফ্রানৎসিস্কা বললেন, একজোড়া ফেন্সি নূতন জুতো কিনবে—দাম চল্লিশ ফ্রাঁ (৩৮)–আমি বললুম, আমার অত টাকা নেই, ফ্রানৎসিস্কা বললে, সে আমার কাছ থেকে টাকা চায় না, তার মা আসছেন দুদিন পরে, তিনি টাকাটা দেবেন। কি আর করি বলুন তো? তদন্ডেই টাকাটা ঝেড়ে দিলুম। ফ্রানৎসিস্কার মা! বাপরে বাপ! আপনি কখনো ম্যান-ইটার বাঘের মুখোমুখি হয়েছেন?’
আমি কিছু বলবার পূর্বেই ফ্রানৎসিস্কা আমাকে বললেন, ‘দোহাই মা-মেরির! এই পেটারটা যে কি মিথ্যাবাদী আপনাকে কি করে বোঝাই? (পেটারের আপত্তি শোনা গেল, ‘ডার্লিং, অশ্লীল গল্পের চেয়ে গালি-গালাজ অনেক বেশি খারাপ’) আমার মা যাতে বড়দিন এক-একা না কাটান তার জন্য নিজে-আমাকে না বলে—লুৎর্সেন গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে এল। তার পর বছরের শেষ রাত্রে তার সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচলে ভোর চারটে অবধি-ওঁর সঙ্গে নাচলে অন্তত পাঁচিশটা নাচ, আমার সঙ্গে দুটো, জোর তিনটে। বুড়িকে শ্যাম্পেন খাইয়ে খাইয়ে টং করিতে দিয়ে, যত সব অদ্ভুত পুরানো রাশান আর পোলিশ নাচ। কখনো সে মাটিতে বসে। উবুন্থাবড়ায়-মা তখন তার চতুর্দিকে পাই পাই করে চক্কর খাচ্ছেন-কখনো বঁদরের মত লম্ফ দিয়ে ছাতে মাথা ঠোকে-মা তখন ১৫ ডিগ্ৰীতে কাত হয়ে স্কার্ট তুলেছেন হাঁটু অবধি। তারপর তাকে কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে বঁই বঁই করে ঘুরলে ঝাড়া দশ মিনিট। বাদবাকি নাচনে-ওলা-নাচনে-ওলীরা ততক্ষণে ফ্লোর তাদের জন্য সাফ করে দিয়ে আপন আপন টেবিলে চলে গিয়েছে। অরকেস্ট্রাও বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে, একটা নাচের জন্য ওরা বাজনা বাজায় দশ, জোর পনের মিনিট-ঐ মাৎসুর্কা না কি পাগলা নাচের জন্যে। ওরা বাজনা বাজালে পাকা এক ঘণ্টা। নাচের শেষে মা তো পড়ল চেয়ারে, ওদিকে কিন্তু চোখ বন্ধ করে বুড়ি মিটমিটিয়ে হাসছে—খুশিতে ডগোমগো!
পেটার বললেন, ‘ডার্লিং, কিন্তু সে রাত্রের সব চেয়ে সেরা নাচের জন্য কে পেল সেটা তো বললে না।’
তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ‘মা পেলেন ফাস্ট প্রাইজ, আমি সেকেন্ড। তাই তো আমি শাশুড়িদের বিলকুল পছন্দ করি নে।’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘আচ্ছা আহাম্মুক তো! নাচের পয়লা প্রাইজ হামেশাই রমণী পায়। দুসরাটা পুরুষ। এটা হচ্ছে শিভালরি। তোমাকে কি করে পয়লা প্রাইজ দিত?’
পেটার আমার দিকে মুখ করে বললেন, ‘গিন্নির রাগ, আমি ওর সঙ্গে নাচলুম না। কেন? আচ্ছা মশায়, বলুন তো, আপনি যদি কবিতা পড়ে শোনান, খোশগল্প করেন, বাজনা বাজান কিংবা কালোয়াতি করেন তবে যে সমে সমে মাথা নাড়তে পারে তাকে আদর-কদর করবেন, না। আপনি স্ত্রীকে? যেহেতু তিনি আপনি স্ত্রী। রসের বাজারে আপনি পর করা যায়?’ আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, ‘তই তো আমি নিবেদন করলুম, ‘যাঁর চরিত্র উদার–অর্থাৎ যিনি রসিক জন—ৰ্তার কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন’।’
পেটার নয়রাট বললেন, ‘গিন্নি অবশ্যি একটা কথা ঠিক বলেছেন, আমরা কেউ এটিকেটের ধার ধারি নে। এ বিষয়ে চমৎকার একটা ‘ট্যুনিস’, ‘শেলে’র গল্প আছে। ‘ট্যুনিস-শেল’ কে চেনেন?’
আমি বললুম, ‘ঠিক মনে পড়ছে না।’
‘আগাগোড়া একটি ‘প্রতিষ্ঠান’ বলতে পারবেন। ‘ট্যুনিস’ কথাটা এসেছে লাতিন ‘আন্তনিয়ুস’ থেকে। আন্তনিয়ুস গালভরা, গেরেমভারী, খানদানী ঐতিহ্যসিক নাম। আর ট্যুনিস অতিশয় প্লিবিয়ান অপভ্রংশ-নামটাতেই তাই একটুখানি রসের আমেজ লাগে।’
আমি বললুম, ‘আমাদের ‘পঞ্চানন’ নামটাও গেরেমভারী কিন্তু তার গাৰ্হস্থ্য সংস্করণ ‘পাঁচু’টাতেও ঐরকম রসসৃষ্টি হয়।
‘তাই নাকি? আপনারাও তাহলে এ রসে বঞ্চিত নন? আর ‘শেল’ কথাটার মানে ‘ট্যারা’। বুঝতেই পারছেন পিতৃদত্ত নাম নয়, পাড়া দত্ত। এবং নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, এরা দুজন ডুক ব্যারন নন-খাঁটি ওয়ার্কিং কেলাস। খায়দায়, ফুতিফর্তি করে, ফোকটে দু পয়সা মারার তালে থাকে, কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ আর বিয়ার-খানায় আড্ডা জমাতে পারলে এরা আর কিছু চায় না।’
‘একদিন হয়েছে কি, ট্যুনিস-শেল রাস্তায় একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে—তা ওরা হামেশাই ওরকমধারা রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়, না হলে গল্পই বা জমবে কি করে?’
ট্যুনিস বললে, ‘চ, শেল; এই দিয়ে উত্তমরূপে আহারাদি করা যাক।’ দুজনা ঢুকল গিয়ে এক রেস্তোরাঁয় আর অর্ডার দিলে দুখানা কটলেটের।
‘ওয়েটার এসে ছুরিকাঁটা আর দুখানা প্লেট সাজিয়ে দিয়ে আনল একখানা বড় ডিশে করে। দুখানা কাটলেট।’
নয়রাট বললেন, ‘কটলেট তো আর অ্যারোপ্লেনের স্ক্রু নয় যে ফিতে দিয়ে মেপেজুপে কিংবা ছাঁচে ঢেলে, ঠিক একই সাইজে বানানো হবে, কাজেই একখানা কটলেট আরেকখানার চেয়ে সামান্য একটু বড় হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?’
ট্যুনিস তাই ঝাপ করে বড় কাটলেটখানা আপন প্লেটে তুলে নিল। শেল চুপ করে। দেখল। তারপর আস্তে আস্তে ছোট কাটলেটখানা তুলে নিয়ে ট্যুনিসকে বললে, ‘ট্যুনিস, তুই আদব-কায়দা একদম জানিস নে।’–যেন নিজে সে মহা খানদানী ঘরের ছেলে।
‘ট্যুনিস শুধালে, ‘কেন, কি হয়েছে?’
‘শেল বললে, ‘ভদ্রতা হচ্ছে, যে ডিশ থেকে প্রথম খাবার তুলবে, সে নেবে ছোট টুকরোটা।’
ট্যুনিস বললে, ‘আ। আচ্ছা, তুই যদি প্রথম নিতিস তবে তুই কি করতিস?’
‘শেল দম্ভ করে বলল, ‘নিশ্চয়ই ছোট কাটলেটটা তুলতুম।’
‘তখন ট্যুনিস বললে, ‘সেইটেই তো পেয়েছিস, তবে ভ্যাচর ভ্যাচর করছিস কেন?’
নয়রাট গল্প শেষ করে খানাতে মন দিলেন।
বলতে পারব না, আমার পাঠকদের গল্পটা কি রকম লাগিল—আমার কিন্তু উত্তম মনে হল, তাই প্রাণভরে খানিকক্ষণ হেসে নিলুম।
নয়রাট বললেন, ‘তই যখন কেউ এটিকেট নিয়ে বড় বেশি কপচাতে শুরু করে। তখনই আমার এই গল্পটা মনে পড়ে আর হাসি পায়। আরে বাবা, সংসারে থাকবি মাত্র দুদিন। তার ভিতর কত হাঙ্গামা কত হুজ্জত। সেই সব সামলাতে গিয়েই প্ৰাণটা খাবি খায়। তার উপর যদি এটিকেটের নাগপাশ দিয়ে সর্বাঙ্গ আর নবদ্বার বেঁধে দাও। (ফ্রানৎসিস্কার আপত্তি শোনা গেল, ‘পেটার, আবার অশ্লীল কথা!’) তবে দম ফেলবে কি করে? হাঁচবার এটিকেট, কাশবার এটিকেট, থুথু ফেলার এটিকেট, গা চুলকাবার এটিকেট-প্ৰাণটা যায় আর কি।’
আমি সায় দিলুম।
তখন নয়রাট শুধালেন, ‘বলুন তো, কি সে জিনিস যা চাষা অনাদরে, তাচ্ছিল্যে, এমন কি বলতে পারেন, ঘেন্নাভরে রাস্তায় ফেলে দেয়, আর ভদ্রলোক সেটাকে ধোপদূরস্ত দামী রুমালে ঢেকে, পকেটে পুরে অতি সন্তৰ্পণে বাড়ি নিয়ে আসেন?’
আমি খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, ‘তা তো জানি নে।’
বললেন, ‘সিকিনি। চাষা ফাত করে রাস্তায় নাক ঝেড়েও ওদিকে আর তাকায় না, ভদ্রলোক রুমাল খুলে ছিক করে তারই উপর একটুখানি নাক ঝেড়ে সেটিকে সযত্নে ভাঁজ করে, পকেটে পুরে বাড়ি ফেরেন।
ফ্রানৎসিস্কা হঠাৎ বললেন, ‘পেটার, তুমি তো বকবক করে এটিকেটের নিন্দাই করে যাচ্ছ, ওদিকে একদম ভুলে গিয়েছে, ভদ্রলোক প্রাচ্যদেশীয়, সেখানে এটিকেটের অন্ত নেই; এদেশে তো প্রবাদই রয়েছে, ‘ওরিয়েন্টাল কার্টাসি’। যে আচার ওঁদের প্রিয় তুমি তাই নিয়ে মাস্করার পর মাস্করা করে যাচ্ছি।’
পেটার বললেন, ‘আদপেই না। আমি তো ভদ্রতার (ম্যানার্স) নিন্দে করছিনা, আমি করছি। এটিকেটের। দুটো তো এক জিনিস নয়।’
তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনাদের দেশে ব্যবস্থাটা কি রকম?’
আমি বললুম, অনেকটা আপনাদের দেশেরই মতো। অর্থাৎ, ভদ্রতরক্ষার চেষ্টা আমরাও করে থাকি তবে এটিকেটের বাড়াবাড়ি দেখলে তাই নিয়ে আপনার-ই মতো টীকাটিপ্পানী কেটে থাকি। তবে কি না ভারতবর্ষ বিরাট দেশ-তার নানা প্রদেশে নানা রকমের এটিকেট। এই ধরুন লক্ষ্মেী। সেখানে কোনো খানদানী বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতে হলে বাড়িতে উত্তমরূপে আহারাদি সেরে যেতে হয়। কারণ, খানার মজলিসে গল্প উঠবে, কোন মৌলানা দিনে আড়াই তোলা খেতেন, কোন সাহেব-জাদা দুই তোলা, কোন পীর-জাদা এক তোলা আর কোন নওয়াব একদম খেতেনই না। অথচ সংস্কৃত আপ্তবাক্য এ বিষয়ে যাঁরা রচনা করেছেন তারা এ এটিকেট আদপেই মানতেন না।’
কর্তা-গিন্নি উভয়েই শুধালেন, ‘আপ্তি-বাক্য কি?’
আমি বললুম,-
‘পরান্নং প্রাপ্য দুৰ্বদ্ধে, মা প্ৰাণেষু দয়াং কুরু।
পরান্নং দুর্লভং লোকে প্ৰাণাঃ জন্মনি জন্মনি।।
অর্থাৎ
ওরে মুর্খ, নেমন্তন্ন পেয়েছিস, ভালো করে খেয়ে নে। প্রাণের মায়া করিস নি, কারণ ভেবে দেখ, নেমন্তন্ন কেউ বড় একটা করে না। বেশি খেয়ে যদি মরে যাস তাতেই বা কি–প্ৰাণ তো ভগবান প্ৰতি জন্মে ফ্রি দেয়, তার জন্য তো আর খর্চা হয় না।’
***
আমি বললুম, চমৎকার রান্না হয়েছে’–রান্না সত্যই মামুলী রান্নার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছিল, পোশাকী রান্না বললেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, রুশ কায়দায় মাছ কি করে রাঁধতে হয়?’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘আপনার বুঝি রান্নার শখ?’
আমি বললুম, ‘না; তবে আমার মা খুব ভালো রাঁধতে পারেন আর নূতন নূতন দিশী-বিদেশী পদ শেখাতে তাঁর ভারি আগ্রহ। আমি প্রতিবার দেশ-বিদেশ ঘুরে যখন বাড়ি ফিরি তখন সবাই আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানা রকম গল্প শোনে, মাও শোনে, কিন্তু বলার প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর তিনি আমাকে একলা-একলি শুধান, নূতন রান্না কি কি খেলুম। আমি ভালো ভালো পদগুলোর নাম করলে পর মা শুধাতেন। ওগুলো কি করে। রাঁধতে হয়। গোড়ার দিকে রন্ধনপদ্ধতি খেয়াল করে শিখে আসতুম না বলে মাকে কষ্ট করে। একসপেরিমেন্ট করে করে শেষটায় পদটা তৈরি করার পদ্ধতি বের করতে হত। এখন তাই মোটামুটি পদ্ধতিটা লিখে নিই; মাকে বলা মাত্রই দুইট্রয়েলের পরই ঠিক জিনিস তৈরি করে দেন।
ফ্রানৎসিস্কা আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘বলেন কি?’
বললুম, হ্যাঁ, আশ্চর্য হবারই কথা। আমিও একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তিনি কোনো পদ না দেখে না চোখে তৈরি করেন কি করে? মা বলেছিলেন,–’এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে-’আরো বাপু, রান্না মানে তো হয় সেদ্ধ করা, নয়। তেলে-ঘিয়ে ভাজা, কিংবা শুকনো শুকনো ভাজা অথবা শিকে ঝলসে নেওয়া। এরই একটা, দুটো কিংবা তিনটে কায়দা চালালেই পদ ঠিক উতরে আসবে। আর তুইও তো বলেছিস আমাদের দেশের বাইরে এমন কোনো মশলা জন্মায় না। যা এদেশে নেই। তা হলে তুই যা বিদেশে খেয়েছিস, আমি তৈরি করতে পারব না কেন?’
তারপর বললুম, ‘অবশ্য মা আমাকে কখনো এসপেরেগাস কিংবা আর্টিচোক খাওয়ান নি কারণ ওগুলো আমাদের দেশে গজায় না। তাই নিয়ে মায়েরও কোনো খেদ নেই-কারণ যে সব শাক-সন্তজী আমাদের দেশে একদম হয় না। সেগুলোর কথা আমি মায়ের সামনে একদম চেপে যেতুম।’
ফ্রানৎসিস্কা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বললেন, ‘ওঃ, পাছে তার দুঃখ থেকে যায়, তিনি তাঁর ছেলের সব প্রিয় খাদ্য খাওয়াতে পারলেন না।’
আমি বললুম, হ্যাঁ। কিন্তু তিনি যে তরো-বেতরো রান্না শেখার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতেন তার আরো একটা কারণ রয়েছে। রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট। আর আমার মা—‘
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘থামলেন কেন?’ আমি লজ্জার সঙ্গে বললুম, ‘নিজের মায়ের কথা সত্যি হলেও বলতে গেলে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে। আপনারা হয়তো ভাববেন ফুলিয়ে বলছি।’
নয়রাট এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এখন হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ‘ব্যস! হয়েছে। আপনাকে আর এটিকেট দেখাতে হবে না। ফ্রানৎসিস্কা আপনাকে বলে নি, এ বাড়িতে এটিকেট বারণ?’
ফ্রানৎসিস্কা তাড়াতাড়ি বললেন, ‘ছিঃ, পেটার, তুমি ওরকম কড়া কথা কও কেন?’
আমি সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বললুম, আদপেই না। ওঁর ধমক থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আপনারা সরল প্রকৃতির লোক, আপনাদের সামনে সব কিছু অনায়াসে খুলে বলা যায়। তা হলে শুনুন, যা বলেছিলুম, রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট বিশেষ আর আমার মা খাঁটি আর্টিস্ট। ঠিক আর্ট ফর আর্টস সেক নয়, অর্থাৎ তিনি মনের আনন্দে খুদ-খুশির জন্য রোধেই যাচ্ছেন, কেউ খাচ্ছে না, কিংবা খেয়েও কেউ ভালোমন্দ কিছু বলছে না-তা নয়। তিনি রান্নার নূতন নূতন টেকনিক শিখতে ভালোবাসতেন সত্যকার আর্টিস্ট যে রকম নূতন নূতন টেকনিক শিখতে ভালোবাসে। আপনি ভালো প্যাস্টেল পেন্টিং করতে পারেন, কিন্তু অয়েলপেন্টিং দেখে কিংবা তার কথা শুনে আপনারও কি ইচ্ছে হবে না। সেই টেকনিক রপ্ত করার? কিংবা আপনি উড়ুকাট করেন—যদি লাইন এনগ্ৰেভিং, এচিং, মেদজোটিন্ট, আকওয়াটিন্টের খবর পান, তবে সেগুলোও আয়ত্ত করার বাসনা আপনার হবে না?
অথচ দেখুন, খাঁটি আর্টিস্ট অজানা জিনিস আয়ত্ত করার জন্য যত উদগ্ৰীবই হোক না কেন, হাতের কাছের সামান্যতম মালমশলাও সে অবহেলা করে না-নানা রঙের মাটি, শাকসব্জী থেকেও নূতন রঙ আহরণ করার চেষ্টা করে।
‘ভারতবর্ষের যে প্রান্তে আমার দেশ, সেখানে সব সময় জাফরান পাওয়া যায় না। তাই মা তারই একটা ‘এরজাৎস’ সব সময়ে হাতের কাছে রাখেন। বুঝিয়ে বলছি
‘আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। শিউলির বেঁটা সুন্দর কমলা রঙের আর পাপড়ি সাদা। ফুল বাসি হয়ে গেলে মা সেই বেঁটাগুলো রোদুরে শুকিয়ে বোতলে ভরে রাখেন। সেই শুকনো বেঁটা গরম জলে ছেড়ে দিলে চমৎকার সুগন্ধ আর কমলা রঙ বেরয়। মেয়েরা সাধারণত ঐ রঙ দিয়ে শাড়ি ছোপায়। মা খুব সরু চালের ভাত ঐ রঙে ছুপিয়ে নিয়ে চিনি, কিসমিস, বাদাম দিয়ে ভারি সুন্দর মিঠাখানা’ তৈরি করেন।
‘এটা মায়ের আবিষ্কার নয়। কিন্তু তবু যে বললুম, তার কারণ প্রকৃত গুণী কলাসৃষ্টির জন্য দেশী-বিদেশী কোনো উপকরণ অবহেলা করেন না।’
নয়রাটদের বাড়িতে এটিকেট বারণ, তবু আপন মায়ের কথা একসঙ্গে এতখানি বলে ফেলে কেমন লজ্জা পেলুম।
***
রুশ কবি পুশকিনের রচিত একটি কবিতার সারমর্ম এই—
‘হে ভগবান, আমার প্রতিবেশীর যদি ধনজনের অন্ত না থাকে, তার গোলাঘর যদি
খ্যাতি-প্রতিপত্তি যদি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তবু তাতে আমার কণামাত্র লোভ নেই; কিন্তু তার দাসীটি যদি সুন্দরী হয় তবে-তবে, হে ভগবান, আমাকে মাপ করো, সে অবস্থায় আমার চিত্তচাঞ্চল্য হয়।’
পুশ্কিন সুশিক্ষিত, সুপুরুষ এবং খানদানী ঘরের ছেলে ছিলেন, কাজেই তার ‘চিত্তদৌর্বল্য’ কি প্রকারের হতে পারত সেকথা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। এইবারে সবাই চোখ বন্ধ করে ভেবে নিন কোন জিনিসের প্রতি কার দুর্বলতা আছে।
আমি নিজে বলতে পারি, সাততলা বাড়ি, ঢাউস মোটরগাড়ি, সাহিত্যিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এ সবের প্রতি আমার কণামাত্র লোভ নেই। আমার লোভ মাত্র একটি জিনিসের প্রতি—অবসর। যখনই দেখি, লোকটার দু’পয়সা আছে অর্থাৎ পেটের দায়ে তাকে দিনের বেশির ভাগ সময় এবং সর্বপ্রকারের শক্তি এবং ক্ষমতা বিক্রি করে দিতে হচ্ছে না। তখন তাকে আমি হিংসে করি। এখানে আমি বিলাসব্যসনের কথা ভাবছি নে পেটের ভাত ‘–’র(১) কাপড় হলেই হল।
অবসর বলতে আমি কুঁড়েমির কথাও ভাবছি নে। আমার মনে হয়, প্রকৃত ভদ্রজন অবসর পেলে আপন শক্তির সত্য বিকাশ করার সুযোগ পায় এবং তাতে করে সমাজের কল্যাণলাভ হয়। এই ধরুন, আমার বন্ধু ‘শ্ৰী ‘ক’ দাশগুপ্ত। বদ্যির ছেলে-পেটে অসীম এলেম, তুখোড় ছোকরা, তালেবর ব্যক্তি। সদাগরী আপিসে কর্ম করে, বড় সাহেবকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়—মোটা তনখা ভী পায়।
বয়স তার এখনো তিরিশ পেরোয় নি। পার্টিশনের পর মারোয়াড়ি কারবারীরা যখন ‘বসকে ঘায়েল করে ব্যবসা কেনবার জন্য উঠে পড়ে লাগল, তখন আমার এই বদ্যির ব্যাটা সায়েবকে এমন সব ‘কৌশাল’ বাতিলালে যে উল্টে ওনারা চোখের জলে নাকের জলে।
সায়েবও বড় নেমকহালাল(২) লোক। প্রায়ই হ্যালো, ড্যাস-গুপটা’ বলে বাড়িতে ঢোকেন, ‘লৌচি’ (লুচি)। খেয়ে যান, ড্যাস-গুপটার ছেলেদের জন্য পূজার বাজারে দু’চারখানা ‘ডোঁটি’ (ধুতিও)ও রেখে যান। আমি বরাবর সকালটা দাশগুপ্তের বাড়িতে কাঁটাই, তাই সায়েবের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোলাকাত হয়ে যায়। লোকটি এদেশে-আসা সাধারণ ইংরেজদের মত গাড়ল নয়, ইংরিজি শোলোক খাসা কপচাতে পারে, অর্থাৎ মধুরকণ্ঠে উচ্চ-স্বরে শেলি-কীটস আবৃত্তি করতে পারে।
সায়েবের কথা উপস্থিত থাক। দাশগুপ্তের কথায় ফিরে যাই।
আমি জানি দাশগুপ্ত কোনো চেম্বার অব কমার্সের বড়কর্তা হবার জন্য লালায়িত নয়। দেড় হাজার টাকার মাইনেকেও সে থোড়াই কেয়ার করে।
আমি জানি, আজ যদি তাকে কেউ পাঁচশ টাকা প্রতি মাসে দেয়, তবে সে কলকাতা শহরের হেথা-হোথা সর্বত্র দশখানা নাইট স্কুল খুলবে। এখন সে আপিসে দিনে সাতঘণ্টা কাটায়—নাইট স্কুল খোলবার মোক পেলে সে পরমানন্দে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা সেগুলোর তদারকিতে, ক্লাস নেওয়াতে কাটাবে। বিশ্বাস করবেন না, সে তার উড়ে চাকরিটাকে স্বাক্ষর করার জন্য উড়ে কায়দায় বর্ণমালা পর্যন্ত শিখিয়েছে-চোখ বন্ধ করে মাথা দুলিয়ে দিব্য বলে যায়,–
‘ক’রে কমললোচন শ্ৰীহরি।
করেন শঙ্খ-চক্ৰধারী।
‘খ’ রে খাগ-আসনে খগপতি।
খাটন্তি লক্ষ্মী-সরস্বতী।।
‘গ’ রে গরুড়-ইত্যাদি—
(আমার সহৃদয় উড়িষ্যাবাসী পাঠকবৃন্দ যেন কোনো অপরাধ না নেন–যদি নামতাতে কোনো ভুল থেকে যায়; আমি দাশগুপ্তের মুখে মাত্র দু’তিনবার শুনেছি; কেউ যদি আমাকে পুরো পাঠটা পাঠিয়ে দেন, তবে বড় উপকৃত হই)।
অর্থাৎ আজ যদি দাশগুপ্তকে পেটের ধান্দায় আপিস না যেতে হয়, তবে সে তার জীবস্মৃত্যুর চরম কাম্য কাজে ফলাতে পারবে। ক ক’লক্ষ মণ পাট কিনল, কে ধাপ্পা এবং ঘুষ দিয়ে ক’খানা ওয়াগন বাগালে তাতে দাশগুপ্তের কোনো প্রকারের চিত্তদৌর্বল্যও (হেথাকার ভাষায় দিলচসপী) নেই। দেড় হাজার টাকার মাইনে কমে গিয়ে পাঁচশ হলে সে দুম করে মোটরখানা বিক্রি করে দিয়ে ট্রামে চড়ে ইস্কুলগুলোর তদারক করবে।
আপনি বিচক্ষণ লোক, আপনি শুধাবেন, এ পাগলামি কেন?
এটা পাগলামি নয়।
আসলে দাশগুপ্ত ইস্কুল মেস্টার। তার বাবা টোলে আয়ুৰ্বেদ শেখাতেন, তার ঠাকুরদাও তাই, তার বাপও তাই, তার উপরের খবর জানি নে।
এবং আমার সুহৃদ যে কী অদ্ভূত ইস্কুল-মেস্টার সে কথা কি করে বোঝাই? চাকরির ঝামেলার মধ্যিখানেও সে একটা নাইট ইস্কুল চালায়।
একদিন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দেখি, সে তার ইস্কুলে ইংরেজি পড়াচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছে, ‘আই গো!’
ছোড়ারা তীব্ৰকণ্ঠে ঐক্যস্বরে বলছে, ‘আই গো!’
‘উই গো!’
‘উই গো!’
‘ইউ গো!’
‘ইউ গো!’
‘উই গো!’
‘হী গোজ!’
‘হী গোজ!’
‘রাম গোজ!’
‘রাম গোজ!’
‘শ্যাম গোজ!’
‘শ্যাম গোজ!’
দাশগুপ্ত সদার-পোড়োর মত বলে যাচ্ছে আর ছোঁড়ারা চিৎকার করে দোহার গাইছে।
সর্বশেষে দাশগুপ্ত লাফ দিয়ে উচ্চতম কণ্ঠে চেঁচোল, ‘রাম অ্যান্ড শ্যাম গো গো গো!’
দাশগুপ্তের স্বপ্ন কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। এমন দিন কখনো আসবে না যে, সে পেটের চিন্তার ফৈসালা করে নিয়ে তামাম শহর নাইট স্কুলে নাইট স্কুলে ছয়লাপ করে দিতে পারে।
দাশগুপ্তের কথা যাক। আমি তার উল্লেখ করলুম নয়রাট-জীবনীটা তুলনা দিয়ে খোলসা করার জন্য।
ইয়োরোপে এ জিনিসটা হামেশাই হচ্ছে।
নয়রাটি মেট্রিক পাস করেন ১৮ বছর বয়সে, সংসারে ঢোকেন। ১৯ বছর বয়সে। তারপর ঝাড়া ছাব্বিশটি বছর ব্যবসা-বাণিজ্য করে পয়তাল্লিশ বছর বয়সে দেখেন এতখানি পুঁজি জমেছে যে, বাকী জীবন তাকে আর সংসার-খরচের জন্য ভাবতে হবে না।
‘টাকা জমানোর নেশা আমাকে কখনো পায় নি। আমি জানি এ দুনিয়ার বহু লোকই আমার ধারণা নিয়ে সংসারে ঢোকে। কিন্তু বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত ধর্মচ্যুত হয়। জীবনে আমার কতকগুলো শখ ছিল–কিন্তু হিসেব করে দেখলুম, –সেগুলো বাগে আনতে হলে পেটের একটা ফৈসাল পয়লাই করে নিতে হবে। তাই খাটলুম ছাব্বিশ বছর ধরে একটানা। আমার অসুখবিসুখ করে না, আমি একদিনের তরে কাজে কামাই দিই নি—ঐ শুধু বিয়ের সময় যে সাতদিন হনিমুনে কাঁটাই বাধ্য হয়ে তারই জন্য ছুটি নিতে হয়েছিল।’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘তা ছুটি নিয়েছিলে কেন? আমি বলি নি, তোমার আপিসঘরে, কিম্বা সেখানে জায়গা না হলে তোমার গুদোমঘরে পাদ্রী ডেকে মন্ত্র পড়লেই হবে।’
নয়রাট বললেন, ‘অন্য মতলব ছিল, ডার্লিং, তোমাকে তো আর সব কিছু খুলে বলি নি।’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘বটে!’
নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনাকে খুলে কই।
‘বিয়ে করেই বউকে নিয়ে চলে গেলুম এক অজ পাড়াগাঁয়ে। সে গাটা খুঁজে বের করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল এবং সে গা থেকেও আধ মাইল দূরে একটি ‘শালে’ ভাড়া নিলুম সাতদিনের জন্য। সেখানে ইলেকটিরিক আছে—ব্যস্ আর কিছু না। জলের কল না, খবরের কাগজ না, দুধওয়ালা দুধ পর্যন্ত দিয়ে যায় না।’
‘রাত্তিরের ডিনার খেয়েই আমরা সে বাড়িতে গিয়ে উঠলুম।
ফ্রানৎসিস্কা বাড়িতে ঢুকেই সোহাগ করে বললে—’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘চোপ।’
নয়রাট বললেন, ‘আচ্ছা, আচ্ছা’ চোপ।’ তারপর আমাকে বললেন, ‘আচ্ছা, তাহলে কমিয়ে-সমিয়ে বলছি-বাদবাকিটা পরে আপনাকে একলা একলি বলব।’
‘ভোর তিনটের সময় আমি চুপসে খাট ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে নোমলুম নিচের তলায়। পিছনের বাগানে গিয়ে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে গেলুম রান্নাঘরে। সেখানে নাকে-মুখে বিস্তর ধুঁয়ো গিলে ধরালুম উনুন। তারপর বেকন ফ্রাই করে, গরম কফি, টেস্ট ইত্যাদি বানিয়ে যাবতীয় বস্তু একখানা বিরাট খুঞ্চাতে সাজিয়ে গেলুম উপরের তলায় ফ্রানৎসিস্কার বিছানার কাছে। আস্তে আস্তে জাগিয়ে বললুম, ‘ব্রেকফাস্ট তৈরি।’
‘ফ্রান্ৎসিসকা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে। (আবার ‘চোপ’ এবং ‘আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ’ শোনা গেল), ‘ডার্লিং’ তুমি আমাকে কত ভালোবাসো-এই ভোরে এই শীতে আমাকে কিছু না বলে তুমি এত সব করেছ।’
‘আমি বললুম, ‘ডার্লিং না। কচু, ভালোবাসা না হাতি। আমি এসব তৈরি করে। আনলুম শুধু তোমাকে দেখাবার জন্য যে, বাদবাকি জীবন তোমাকে এই রকম ধারা করতে হবে। আর আমি শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খাবো।’
আমি প্রাণ খুলে হাসলুম।
দেখি নয়রাটও মিটমিটিয়ে হাসছেন। ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘আপনি এই তাড়িখানার বেহুদা প্ৰলাপটা বিশ্বাস করলেন?’
আমি বললুম, ‘কেন করব না? শাদীর পয়লা রাতে শুধু ইরানেই নয়, আরো মেলা দেশে মেলা বর বেড়াল মেরেছে, এ তো আর নূতন কথা কিছু নয়। এবারে সুইস সংস্করণটি শেখ হল এই যা।’
দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, ‘সে আবার কি?’
আমাকে বাধ্য হয়ে শাদীর পয়লারাতে বেড়াল মারার গল্পটা বলতে হল, কিন্তু নয়রাটের মত জমাতে পারলুম না।–রাসিয়ে গল্প বলা আমার আসে না, সে আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন।
দুজনেই স্বীকার করলেন, ইরানী গল্পটাই ভালো।’(৩)
তখন ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘পেটারের বকুনিতে অনেকগুলো ভুল রয়েছে। প্রথমত আমরা হনিমুন যে বাড়িতে কাঁটাই, সেখানে গ্যাস ছিল, উনুন ধরাবার কথাই ওঠে না, দ্বিতীয়ত পেটার ককখনো ব্রেকফাস্ট খায় না এবং সর্বশেষ বক্তব্য, যে-ব্রেকফাস্টের বর্ণনা সে দিল সেটা ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। কোনো কনটিনেন্টাল শূয়ারের মতো ব্রেকফাস্টের সময় একগাদা বেকন আর আণ্ডা গেলে না। পেটার গল্পটা শুনেছে নিশ্চয়ই কোনো ইংরেজের কাছ থেকে, আর সেটা পাচার করে দিলে আপনার উপর দিয়ে।’
পেটার বললেন, ‘রোমব্রান্ট একবার এক ভদ্রলোকের মায়ের পট্রেট একেছিলেন। ভদ্রলোক ছবি দেখে বললেন, ‘তাঁর মায়ের সঙ্গে মিলছে না। রেমব্রান্ট বললেন, ‘একশ বছর পর আপনার মায়ের সঙ্গে কেউ এ ছবি মিলিয়ে দেখবে না।–তারা দেখবে ছবিখানি উতরেছে কিনা।’
তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘গল্পটি ভালো কি না সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। ঘটেছিল কি না, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর; আপনি কি বলেন?’
আমি বললুম, ‘সুন্দর-ই সত্য-না ঘটলেও ঘটা উচিত ছিল।’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘বটে!’
নয়রাট বললেন, ‘আমার শখ ছিল দাবা-খেলাতে এবং সে ব্যসনে মেতে আমার কত সময়-সামর্থ্য বরবাদ গিয়েছে তার হিসেবা-নিকেশ আমি কখনো করি নি। দাবা-খেলা আমি
রোজ রাত্তিরে বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। এক রাত্রে আসতে পারলেন না জোর বরফের ঝড় বইছিল ব’লে, আর ওদিকে বাবা তো মৌতাতের সময় হন্যে হয়ে উঠলেন। আমি থাকতে না পেরে বললুম, ‘তা আমার সঙ্গেই খেলো না কেন?’ বাবা তো প্রথমটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু জানেন তো, দাবার নেশা কী নিদারুণ জিনিস-বরঞ্চ মদের মাতাল খুনীর সঙ্গে এক টেবিলে মদ খেতে রাজী হবে না, দাবার মাতাল তার সঙ্গে খেলতে কণামাত্রও আপত্তি জানাবে না। বাবা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যাভরে খেলতে বসলেন, প্রথম দু’বাজি জিতলেনও কিন্তু তৃতীয় বাজি হল চালমাত এবং তারপর তিনি আর কখনো জেতেন নি। তবে তার হল বুড়ো হাড়, এখনো খুব শক্ত শক্ত চালের চমৎকার চমৎকার উত্তর বাতলে দিতে পারেন।’
আমার আশ্চর্য লাগল, কারণ শরৎ চাটুজ্জেও কৈলাস খুড়োর বর্ণনাতেও ঐ কথাই বলেছেন; খুড়োর শেষ বয়সে আটপৌরে খেলা ভুলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য খেলোয়াড়রা তার কাছে যেত। সে কথাটা নয়রাটকে বলতে তিনি বললেন, ‘অতিশয় হক কথা। পৃথিবীতে মেলা ধৰ্ম আছে—তাই ক্রীশচান, জু এবং দাবাড়ে। দাবাখেলা ধর্মের পর্যায়ে পড়ে, আর যারাই এ ধর্ম মানে তারা সব-ভাই-সব-ব্রাদার। দাবাড়েদের ‘পেনফ্রেন্ড’ পৃথিবীর সর্বত্র যে রকম ছড়ানো তার সঙ্গে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না।’
তারপর বললেন, ‘সেই যে বাবা দাবা ধরিয়ে দিলেন তারপর ওর হাত থেকে আমি আর রেহাই পাইনি। একবার এক পািড় মাতালকে বলতে শুনেছিলুম, সে নাকি জীবনে মাত্র একবার মদ খেয়েছে। আমরা সবাই আসমান থেকে পড়লুম, উলুকটা বলে কি-উদয়াস্ত যে লোকটা ‘ট্যানিসে’র উপর থাকে, সে কি না জীবনে কুন্নে একটিবার মদ খেয়েছে! বেহেড মাতাল এরেই কয়। তখন মাতাল বললে সে মদ খেয়েছে একবারই-তারপর থেকে এ অবধি শুধু তার খোঁয়ারিই ভাঙছে।’
আমি বললুম, ‘ওমর খৈয়াম এ বাবদে যা নিবেদন করেছেন সেটা ঠিক হুবহু এর সঙ্গে খাপ খায় না, তবু অনেকটা এরই কান ঘেষে। খৈয়াম বলেছেন, ‘রোজার পয়লা রাত্রিতে অ্যায়সা পীনা পীউংগা যে তারই নেশার বেঙুণীতে কেটে যাবে রোজার ঝাড়া পুরো মাসটা। ইশ হবে ঈদের দিন। ঈদ মানে পরব। (পরবpar excellence), পরব মানতে হয়, না। হলে জাত যাবে, ধর্ম যাবে, তাই তখন ফের বসে যাব সুরাহী পেয়ালা প্রিয়া নিয়ে।’ তারপর খৈয়াম কি করেছিলেন সে হদিস তার রুবাইতে মেলে না, তবে বিবেচনা করি, দুসরা রমজান তক তিনি তাঁর কায়দা-কানুনে কোনো রদবদল করেন নি।’(৪)
ফ্রানৎসিস্কা এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এখন বললেন, ‘আমি তো এ রুবাই ফিটজিরান্ডে পাই নি। আপনি কি ফার্সীতে পড়েছেন?’
আমি বললুম, ‘ফিটজিরাল্ড তো তর্জমা করেছেন মাত্র বাহাত্তর না বিরাশীটি রুবাইয়াৎ। ওমরের নামে প্রচলিত আছে আট শ’ না এক হাজার, আমি ঠিক জানি নে। তবে এ রুবাইটি আপনি নিশ্চয়ই হুইনসফিল্ড কিংবা নিকোলার অনুবাদে পাবেন। ওঁরা ওমরের প্ৰায় কোনো রুবাই-ই বাদ দেন নি।’
ফ্রানৎসিস্কা শুধালেন, ‘আপনি যে বললেন, ‘ওমরের নামে প্রচলিত রুবাইয়াৎ’ তার অর্থ কি? আপনি কি বলতে চান, এগুলো ওমরের রচনা নয়?’
আমি বললুম, ‘গুণীদের মুখে শুনেছি, ওমরের বেশির ভাগ রুবাইয়াতের মূল বক্তব্য ছিল, ‘এই বিরাট বিশ্ব-সংসার কোন নিয়মে চলে, কি করলে ঠিক কর্মকরা হয় এসব বোঝা তোমার আমার সাধ্যের বাইরে। অতএব যে দুদিন এ সংসারে আছ সে দুদিন ফুর্তি করে নাও; মরার পর কে কোথায় যাবে, কি হবে, না হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।’ তারপর থেকে অন্য যে কোনো কবি এই মতবাদ প্রচার করে নূতন রুবাই লিখতেন। তিনি তক্ষুনি সেটা ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। তার কারণও সরল। ওমর রাজানুগ্রহ পেয়েছিলেন, প্রধান মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলুকও ছিলেন তার ক্লাসফ্রেন্ড। তাই তিনি নিৰ্ভয়ে ইসলাম-বিরোধী এই চার্বাকী মতবাদ প্রচার করে যেতে পেরেছিলেন; কিন্তু পরের আমলে আর সব কবির সৌভাগ্য তা হয় নি-তারা মোল্লাদের বিলক্ষণ ডরাতেন। তাই তারা তাদের বিদ্রোহী মতবাদ ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপন প্ৰাণ বাঁচাতেন-ওদিকে যা বলবার তাও প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে যেতেন।
তাই দেখতে পাবেন, হাফিজের (এবং অন্য আরও কয়েক কবির) দিওয়ানে (তথাকথিত ‘কমগ্ৰীট ওয়ার্কসে) ওমরের কবিতা, আবার ওমরের দিওয়ানে হাফিজের কবিতা। এ জট ছাড়িয়ে ওমরের কোনগুলো, হাফিজের কোনগুলো সে বের করা আজকের দিনে অসম্ভব।’
নয়রাট বললেন, ‘আপনাদের ওমর কোনো কম্মের নয়। তার স্বৰ্গপুরীর বর্ণনাতে তিনি বলেছেন,
“সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে,
ছন্দ গেথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি তার কাছেতে
গুঞ্জে তবে মঞ্জু সুর
সেই তো সখি, স্বৰ্গ আমার,
সেই বনানী স্বৰ্গপুর।”
‘অত সব বায়নাক্কার কী প্রয়োজন!
‘এক দাবাতেই যখন তাবৎ কিস্তি মাত হয়?’
ফ্রানৎসিস্কা শুধালেন, ‘ওমর সম্বন্ধে নানারকমের আজগুবী গল্প শোনা যায়— আমার মন সেগুলো মানতে রাজী হয় না, কিন্তু সেগুলো মানা না-মানার চেয়েও বড় প্রশ্ন, খুদ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে, ইস
করলেন কোন সাহসে? বুঝলুম না হয় রাজা আর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে রক্ষা করছিলেন। কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয়। সে যুগে দেশের পাঁচজন কি ভাবতো না ভাবতো তার হয়ত খুব বেশি মূল্য ছিল না। কিন্তু মোল্লা সম্প্রদায়? সে যুগের রাজারাও তো ওদের সঙ্গে b6(5* ‘
আমি বললুম, হ্যাঁ, কিন্তু ভেবে দেখুন তো, রাজাতে পোপেতে যদি ঝগড়া লাগে তবে শেষ পর্যন্ত কি হয়? হুকুম চালাবার জন্য রাজারা সৈন্যের উপর নির্ভর করেন। সৈন্যরা যদি রাজার প্রতি সহানুভূতি রাখে তবে তারা হুকুম পাওয়া মাত্রই মোল্লাদের ঠ্যাঙাতে রাজী; পক্ষাস্তরে তারা যদি মোল্লাদের মতবাদে বিশ্বাস রাখে। তবে তারা বিদ্রোহ করে, অর্থাৎ রাজাকে ধরে ঠ্যাঙায়।
‘এ তো হল কমন-সেন্স। তাই এস্থলে প্রশ্ন ইরানের লোক সে আমলে কতখানি ইসলাম-অনুরাগী ছিল?
ইতিহাস থেকে আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে-কিন্তু থাক, এসব কচকচানি হয়ত হ্যার নয়রাট পছন্দ করছেন না—’
নয়রাট বললেন, ‘ফের এটিকেট? আর এটিকেট হলেই বা-আমি আপনার বক্তব্যটা শুনছি ইন টার্মস অব চেস। আপনি এখন ওপনিং গেম আরম্ভ করেছেন, তারপর মিডু গেম আসবে—আমি দেখছি আপনি যুঁটিগুলো কি কায়দায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—যা বলছিলেন বলে যান।
আমি বললুম ইরানের সভ্যতা সংস্কৃতি আরবদের চেয়ে বহু শত বৎসরে খানদানী। ইরান ইসলাম প্রচারের বহু পূর্বেই রাজ্য-বিস্তার করতে গিয়ে গ্ৰীসের সঙ্গে লড়েছে, ভারতের পশ্চিম-সীমান্ত দখন করেছে, মিশরীদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে, রোমানদের বেকাবু করেছে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হিসেবে ইরান বহু শত বৎসর ধরে পৃথিবীর পয়লা শক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। পৃথিবীর সম্পদ ইরানে জড়ো হয়েছিল বলে ইরানীরা যে স্থাপত্য, যে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিল তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো কলানিদর্শন আজও পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। আর বিলাসব্যসনের কথা যদি তোলেন তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস ইরানীরা যে রকম পঞ্চেন্দ্ৰিয়ের পূর্ণতম আনন্দ গ্ৰহণ করেছে সেরকম ধারা তাদের পূর্বে বা পরে কেউ কখনো করতে পারে নি।
‘এই ধরুন না, আরব্য-উপন্যাস। অথচ বেশির ভাগ গল্পে যে ছবি পাচ্ছেন সেগুলো আরবের নয়, ইরানের–আমার ব্যক্তিগত ’ফেন্সি’ মত নয়, পণ্ডিতেরা এ কথাই বলেন।
‘মনে পড়ছে সেই গল্প?—যেখানে এক সুন্দরী তরুণী এসে এক ঝাঁকামুটিকে নিয়ে চলল হরেক রকমের সওদা করতে। মাছমাংস ফলমূল কেনার পর সে তরুণী যে সব সুগন্ধি দ্রব্য কিনল। তার সব কটা জিনিসের অনুবাদ কি ইংরিজি, কি ফরাসি, কি বাঙলা কোনো ভাষাতেই সম্ভব হয় নি-করণ, এসব জিনিসের বেশির ভাগই আমাদের অজানা। এমন কি আজকের দিনের আরবরা পর্যন্ত সে-সব বস্তু কি, বুঝিয়ে বলতে পারে না। তুলনা দিয়ে বলছি, আজকের দিনে প্যারিসে যে পাঁচশ’ রকমের সেন্ট বিক্রি হয় সেগুলার বয়ান, ফিরিস্তি, অনুবাদ কি এসকিমো ভাষায় সম্ভবে?
ইরানের তুলনায় সে-যুগে আরবরা ছিল প্যারিসের তুলনায় অনুন্নত–অর্থাৎ সভ্যতা-সংস্কৃতি নিম্ন পর্যায়ে। সেই আরবরা যখন ধর্মের বাঁধনে একজোট হয়ে ইরানে হানা দিল তখন বিলাস-ব্যসনে ফুর্তি-ফার্তিতে বে-এক্তেয়ার ইরানীরা লড়াইয়ে হেরে গেল। আপনাদের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে গ্ৰীস-রোমের কাহিনী বলতে হয়, সে কাহিনী আমরা বলার প্রয়োজন নেই। সেটা হবে ‘সুইটজারল্যান্ডে ঘড়ি আনার মত’।
ইরানীরা মুসলমান হয়ে গেল, কেন হল সে-কথা আরেকদিন হবে, যারা হতে চাইল না অথচ জানত দেশে থাকলে অর্থনীতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন হতেই হবে, তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল আমার দেশ ভারতবর্ষে-সে। ইতিহাসও এস্থলে অবান্তর।
আরবরা মরুভূমির সরল, প্রিমিটিভ মানুষ; তারা ইরানের বিলাসব্যভিচার দেখে স্তম্ভিত-’শক্ট্’, ‘আউট-রেজড্’। আবার ইরানীরাও আরবদের বেদুইন ধরন-ধারণ দেখে ততোধিক স্তম্ভিত এবং ‘শক্ট্’।
‘তদুপরি আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আরবরা সেমিটি বংশের (ইহুদী গোত্রের সঙ্গে তাদের ‘মেলে), আর ইরানীরা আর্য। জীবনাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন; ধর্ম এক হলে কি হয়? প্যারিসের ক্রীশচান। আর নিগ্রো ক্রীশচান কি একই ব্যক্তি?
‘এইবার মোদ্দা কথায় ফিরে যাই; ইরানীরা মুসলমান হল বটে (এবং এদের অনেকেই খাঁটি মুসলিম)। কিন্তু তাদের মজ্জাগত মদ্যাদি পঞ্চমকার ছাড়তে পারলো না। তাই ইরানের জনসাধারণ ওমরের মধ্য-দর্শনবাদ খুশিসে বরদাস্ত করে নিল।
‘দেশের লোক যখন গোপনে গোপনে মদ খায়। তখন রাজার আর কি ভাবনা? মোল্লারা যা বলে বলুক, যা করে করুক-এবং একথাও রাজার অজানা ছিল না যে, বহু লোক আপন হারেমে বসে ঐতিহ্যগত মদ্যপানে কার্পণ্য করেন না।
‘তাই ওমর বেঁচে গেলেন, রাজাও কোনো মুশকিলে পড়লেন না।’
***
নয়রাট বললেন, ‘আপনাদের ওমর খৈয়াম যা আমার ট্যুনিস-শেলও তা।’
আমি ঠিক বুঝতে না পেরে শুধালুম, ‘ট্যুনিস-শেল নিয়ে তো সব রসিকতার গল্প, আর খৈয়াম তো রচেছেন চতুষ্পদী।’
নয়রাট বললেন, ‘মিলটা অন্য জায়গায়। আপনিই বললেন না, দুনিয়ার যত ঈশ্বরবিদ্রোহী, মধ্যোৎসাহী চতুষ্পদী—তা সে ওমরের হোক, হাফিজের হোক, আত্তারের হোক, সব কটা এসে জুটেছে ওমরের চতুর্দিকে, ঠিক তেমনি রসিকতার গল্পে নায়ক যদি মাত্র দুজন হয়, আর তার একজন আর একজনের উপর টেক্কা মারার চেষ্টা করে তবে শেষ পর্যন্ত সেগুলো ট্যুনিস-শেলের নামে চালু হবেই হবে। এগুলোকে তাই সাইকল (চক্র) বলা হয়। ওমর সাইকল, ট্যুনিস-শেল সাইকল কিম্বা পলডি সাইকল। ওমর যেরকম ইরানের, ট্যুনিসশেল তেমনি জর্মনীর কলোন শহরের আবার পলডি সুইটজারল্যান্ডের। আপনাদের ভারতবর্ষে এরকম সাইকল আছে?’
আমি বললুম, ‘এস্তার! হর-পার্বতী সাইকল, গোপালভাঁড় সাইকল, শেখ চিল্লী সাইকল এবং আরো বিস্তর। কিন্তু পলডি সাইকলের বিশেষত্ব কি?’
নয়রাট বললেন, ‘পল্ডি হলেন অতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে, উত্তম বেশভূষায় ছিমছাম না হয়ে বেরোন না, সকলের সঙ্গে অতিশয় ভদ্র ব্যবহার-এ তো সব হল; কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তিনি একটি পয়লা নম্বরের বক্কেশ্বর, আনাড়ির চূড়ামণি-বে-অকুফের শিরোমণি। দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি।–’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘কিন্তু প্লীজ, অশ্লীলগুলো না।’
নয়রাট বেদনাতুরতার ভান করে বললেন, ফ্রানৎসিস্কাকে নিয়ে ঐ তো বিপদ। একশ বার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, শ্ৰীল-অশ্লীল-একেবারে স্বতঃসিদ্ধরূপে, অর্থাৎ perse-পৃথিবীতে নেই, যেরকম নিজের থেকে ‘ডাৰ্ট’ বা ময়লা বলে কোন জিনিস হয় না। অস্থানে পড়লেই জিনিস ডার্ট হয়। ডাস্টবিনের ভিতরকার ময়লা ময়লা নয়-একথা কেউ বলে না, ‘ডাস্টবিন ময়লা হয়ে গিয়েছে, ওটা সাফ করো’, বলে, ‘ডাস্টবিন ভর্তি হয়ে গিয়েছে।’ ঠিক তেমনি সুন্দরীর ঠোঁটের উপর লিপস্টিক ডার্ট নয়, কিন্তু যদি সেই লিপস্টিক আমার গালে লেগে যায়-’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘পেটার! আবার!’
আমার মনে হল, ফ্রানৎসিস্কা বাড়াবাড়ি করছেন, তাই নয়রাটকে সমর্থন করার জন্য গুনগুন করলুম,
‘অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি’
দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, ‘মানে?’
আমি সালঙ্কার সবিস্তর নন্দকুমার গণ্ডে চন্দ্রাবলীর তাম্বলরাগের বর্ণনা দিলুম।
নয়রাটিকে আর পায় কে?–চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, ‘শুনলে, গিন্নি শুনলে? শ্ৰীকৃষ্ণ ভারতীয়দের স্বয়ং ভগবান, আমাদের যেরকম যীশুখ্ৰীষ্ট। তিনি যদি রাধা। ভিন্ন অন্য রমনীকে দয়া দেখাতে পারেন, তবে আমার গালে কিংবা ইভনিং শার্টে লিপস্টিক আবিষ্কার করলে তুমি মর্মাহত হও কেন?’
ফ্রানৎসিস্কা বাধা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কী ঢিড্ মিথ্যেবাদী রে, বাবা! আমি আর মা-বোন ভিন্ন অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে যে পুরুষ-স্থা পুরুষই বটে-শব্দের জন্য পকেট-ডিক্সনরি বের করে তার গালে লিপস্টিক! ডু লিবার হার গট ফন বেনটাইম (বাঙলায়—’হে পিণ্ডিদাদন খানের মা কালী!’)’
আমি বললুম, ‘কিন্তু হ্যার নয়রাট, একটা ভুল করবেন না। দেবতা যা করবার অধিকার রাখেন, সাধারণ মানুষের তা নেই। কিন্তু সে কথা থাক, শ্ৰীল-অশ্লীল সম্বন্ধে আপনি কি যেন বলছিলেন?’
নয়রাট বললেন, ‘Perse’ বাইইটসেলফ যে রকম ডার্ট হয় না, ঠিক তেমনি স্ব-হকে কোনো জিনিস অশ্লীল নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি,–যেখানে বাইবেল পাঠ হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ পেটের ব্যামো নিয়ে আরম্ভ করা অশ্লীল এবং তার চেয়েও ভালো দৃষ্টান্ত, ডাক্তাররা যেখানে যৌন সম্পর্কের আলোচনা করছেন, সেখানে বেমক্কা বাইবেল পাঠ আরম্ভ করা তার চেয়েও বেশি অশ্লীল।
অর্থাৎ বক্তব্য বস্তু প্রতীয়মান, জাজ্জ্বল্যমান করার জন্য যে কোন দৃষ্টান্ত, যে কোন তথ্য, যে কোন গল্প অশ্লীল—তা সে পচিশবার দাস্তের বয়ানই হোক, গণিকাজীবনকাহিনীই হোক। পক্ষান্তরে ইররেলেভেন্ট আউট অব প্লেস (বেমক্কা) জিনিস, তা সে ধৰ্মসঙ্গীতই হোক আর টমাস আকুনিয়াসের জীবনই হোক।’
আমার আশ্চর্য লাগল। কারণ দেশে ভটচাজ মসাই (পাদটীকা’’ দ্রষ্টব্য) এবং কাবুলের মৌলানা মীর আসলাম (‘দেশে-বিদেশে’ দ্রষ্টব্য)। ঐ একই কথা বলেছিলেন।
আমি বললুম, ‘খাটি কথা। কিন্তু এসব থাক না এখন। বরঞ্চ একটা পলডি গল্প বলুন।’
নয়রাট বললেন, ‘সেই ভালো।’ ‘পিয়ন পলডিকে মনি অর্ডারের টাকা দিলে। পলডি দিল জোর টিপস। পাশে বসেছিলেন বন্ধু, তিনি বললেন, ‘পলডি, অত বেশি টিপস দিলে কেন?’ পলডি পরম সন্তোষ সহকারে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে বললে, ‘ঐ তো! কিসসু জানো না, কিসসু সমঝো না; জোর টিপস দিলে ঘন ঘন মনি অর্ডার নিয়ে আসবে না?’
আমার হাসি শেষ হবার পূর্বেই নয়রাট বললেন, কিংবা ধরুন, পলডির বুকে ব্যথা। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে বুক-পিঠ বাজিয়ে বললেন, ঠিক ডায়গনোজ করতে পারছি নে। তবে মনে হচ্ছে অত্যধিক মদ্যপানই কারণ।’
পলডি হেসে বললেন, ‘তই নিয়ে বিচলিত হবেন না, ডাক্তার, আমি না-হয় আরেকদিন আসব, যেদিন আপনি অত্যধিক মদ্যপান করে মাতাল হয়ে যান নি।’
নয়রাট বললেন, ‘পলডি রসিকতাতে শুধু থাকে রস। ও-গুলোর ভিতর দিয়ে পলডির দেশ, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু ট্যুনিস-শেলের গল্পের ভিতর দিয়ে জর্মনি, কলোনের শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের জীবনধারণ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায় এবং তাতে করে গল্পগুলো বেশ একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রঙ ধরে। এই ধরুন পাদ্রী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমরা প্রায়ই ব্যঙ্গ করে থাকি। তারই একটা ট্যুনিস-শেল সাইক্লে বেশ খানিকটে রসের সৃষ্টি করেছে।
ট্যুনিস আর শেল একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে (কাঁটলেটের গল্পে পূর্বেই বলেছি তারা হরদম রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়) এবং ঝগড়া লেগে গিয়েছে টাকাটার ওপর কার হক্ক। ট্যুনিস বলে সে আগে দেখেছে; শেল বলে সে আগে কুড়িয়ে নিয়েছে এবং পজেশন ইজ থ্রি-ফোর্থ অব ল’। তারপর এ বলে ও মিথ্যেবাদী ও বলে এ মিথ্যেবাদী। করতে করতে হঠাৎ ট্যুনিস বললে, ‘তাই সই, মিথ্যেবাদী হওয়াটাও কিছু সোজা কর্ম নয়, আমি হচ্ছি পোড় মিথ্যেবাদী আর তুই হচ্ছিস পেচি (এমেচার) মিথ্যেবাদী।’ শেল বললে,
‘তখন স্থির হল পাল্লা দিয়ে দুজনে মিথ্যে কথা বলবে, যে সব চেয়ে বেহুদা বেশিরম মিথ্যে বলতে পারবে, টাকাটা সে-ই পাবে।
তখন ট্যুনিস বিসমিল্লা বলে আরম্ভ করলে,–
‘পরশুদিন ঘরে মন টিকছিল না বলে বাইরে এসে এক লম্ফে চলে গেলুম আমেরিকায়। সেখানে পৌঁছলুম এক সমুদ্রপারের লিডোতে। দেখি হাজার হাজার মেয়েমদ সেখানে চান করছে, সাঁতার কাটছে। আর ছুড়িগুলো কী বেহায়া! আমার এই একটা নেকটাইয়ের কাপড় দিয়ে তিনটে মেয়ের সুইমিং কস্ট্রম হয়ে যায় (ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘পেটার, আবার?’ নয়রাট বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, টাপোটোপে বলছি’ ) আমার ভয়ঙ্কর রাগ হল। করলুম কি, সব কটা হুলো-মেনিকে ধরে একটা ব্যাগে পুরে দিলুম আরেক লাফ। এবারে পৌঁছলুম, ফুজি-আমা পাহাড়ের কাছে। ব্যাগের ভিতর তিন হাজার বেড়াল ক্যাঁও ম্যাও করছিল বলে আমার দারুণ বিরক্তি বোধ হল। তাই আস্ত ব্যাগটা গিলে ফেলে গোটা আড়াই ঢেকুর তুললুম, তারপর-’
‘শেল বাধা দিয়ে বললে, ‘এতে আর মিথ্যে কোনখানটায় হল? আমি তো তোর সঙ্গেই ছিলুম, পষ্ট দেখলুম, তুই এসব করছিলি।’’
ফ্রানৎসিস্কা গল্পটা আগে শোনে নি বলে হাসলেন। আমিও বললুম, ‘এ গল্পটা ভারি নতুন ধরনের। শেলের উত্তরটা অত্যন্ত আচমকা একটা ধাক্কা দিলে।’
নয়রাট বললেন, ‘গল্পটা এখনো শেষ হয় নি।’
আমরা বললুম, ‘সে কি কথা?’
চীনা পদ্ধতি এসে গিয়েছে। এ গল্পে দুটো ‘সারপ্রাইজ’, কিংবা বলতে পারেন দুটো কিক আছে। খুলে বলছি;
‘ট্যুনিস আর শেল যখন রাইন নদীর পাড়ের রেলিঙে ভর করে মিথ্যের জাহাজ ভাসাচ্ছিল, তখন এক পাস্ত্রী সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যস্তসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন। অনিচ্ছায় কিংবা স্বেচ্ছায়ও হতে পারে, ট্যুনিস শেলের বিকট মিথ্যের বহর তার কানে এসে পৌঁছেছিল। থাকতে না পেরে বললেন, ‘ছি, ছি, বাছারা; এ-রকম ডাহা মিথ্যে তোমরা মুখ দিয়ে বার করছে কি করে? জানো না, মিথ্যা কথা মহাপাপ? আমি জীবন কখনো মিথ্যা বলি নি।’
‘ট্যুনিস পাদ্রীর কথা শুনে প্রথম হ’কচাকিয়ে গেল, তারপর থ মেরে গেল। সম্বিতে ফিরে শেষটায় ক্ষীণকণ্ঠে, বাজি হারার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শেল্কে বললে, “ভাই শেল্ নোটটা ওকেই দে, টাকাটা ওরই পাওনা। তুই এ-রকম পাঁড় মিথ্যে বলতে পারবি নে; আন্মো পারবো না।’’
আমি বললুম, ‘খাসা গল্প; এটা মনে রাখতে হবে।’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘কিন্তু আমি জানি, পেটার ওখানে থাকলে প্রাইজটা সে-ই পেত।’
আমি নয়রাটকে বললুম, ‘গল্পটি সুন্দর, কিন্তু এতে টিপিকাল কলোনের কি আছে? আমাদের মোল্লা-পুরুত সম্বন্ধেও তো এরকম বদনাম আছে।’
নয়রাট বললেন, ‘আমি জানতুম না। তবে শুনুন আরেকটা-আর এর জবোব আপনি দিতে পারবেন না!
‘ট্যুনিস-শেল আবার একখানা দশ টাকার নোট পেয়েছে (ট্যুনিস-শেল সাইক্লের ভিতরে এ হচ্ছে ‘নোটের সাব-সাইকেল’)। এবারে ঝগড়া হয় নি। দুজনে সেই টাকা দিয়ে মদ খেয়ে বেহুঁশি হয়ে পড়েছে রাস্তায়। পুলিশ তাদের পৌঁছে দিয়েছে হাসপাতালে। সকালবেলা তাদের ঘুম ভেঙেছে আর নেশা কেটেছে। দেখে চতুর্দিক ফিটফট, ছিমছাম। ট্যুনিস শুধালে, ‘ওরে শেল, এ আবার এলুম কোথায়?’ শেল বললে, ‘আমিও তাই ভাবছি। দাঁড়া, দেখে আসছি।’
‘শেল গেল। ঘরের বাইরে। পাঁচ সেকেন্ডের ভিতর ছুটে এসে বললে, ‘ওরে ট্যুনিস–আমরা ভারতবর্ষে পৌঁছে গিয়েছি।–রাতারাতি আমাদের ভারতে পাচার করে দিয়েছে।’
ট্যুনিস তো তাজ্জব। শুধালে, ‘কি করে জানলি?’
‘বললে, ‘করিডরে মোটা হরপে লেখা আছে, ‘Die Toiletten befinden sich auf jenseits des Ganges’.’
নয়রাট বললেন, ‘অর্থাৎ, ‘করিডরের দুপাশে বাথরুমের ব্যবস্থা আছে।’ এখন ‘করিডর’ শব্দ জর্মনে Gang আর Gang-এর দুপাশে–অর্থাৎ ষষ্ঠীতৎপুরুষ Ganges, তার মানে বাথরুম গঙ্গার (নদীর) দুপারে।’
‘তই ট্যুনিস-শেল রাতারাতি ভারতে পৌঁছে গিয়েছে।’
নয়রাট বললেন, ‘দেশভ্রমণের গল্পই যদি উঠল। তবে সেই সাব-সাইক্লই চলুক।’
আমি বললুম, ‘উত্তম প্রস্তাব।’
নয়রাট বললেন, ট্যুনিস-শেল পেটের ধান্দায় হামবুর্গ গিয়ে জাহাজের খালাসির চাকরি নিয়ে পোঁচেছে গিয়ে ইস্তাম্বুল শহরে, সেখানে–’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘না, পেটার, ওটা চলবে না।’
নয়রাট ব্যথা-ভরা নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, ‘গল্পটা কিন্তু ছিল খাসা; তার আর কি করা যায়! তবে তাদের নিয়ে যাই নিউ ইয়র্কে।
‘হয়েছে কি, টুনিসের এক মামা নিউ ইয়র্কে দুপয়সা রেখে মারা গিয়েছে। ট্যুনিস উকিলের চিঠি পেয়েছে তাকে সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নিজের সনাক্ত দিয়ে টাকাটা ছাড়িয়ে আনতে হবে। ওদিকে ট্যুনিস আবার ভয়ানক ভীতু ধরনের লোক। এক বিদেশ যেতে ডরায়-শেলকে বললে, ‘ভাই, তুই চ।’ শেল ভাবলে—আর আমিও তাই ভাবতুম–মন্দ কি, ফোকটে মার্কিনমুলুকটা দেখা হয়ে যাবে।
‘তারা নিউ ইয়র্ক পৌঁছিল। ঠিক বড়দিনের দিন। তামাম মার্কিন দেশ বেঁটিয়ে এসে জড়ো হয়েছে নিউ ইয়র্কে পরাব করার জন্য, সব হোটেল আগাগোড়া ভর্তি, করিডরে পর্যন্ত ক্যাম্প কটু পেতে শোবার ব্যবস্থা ফালতো গেস্টদের জন্য করা হয়েছে।
‘মহা দুর্ভাবনায় পড়ল দুই ইয়ার। ডিসেম্বরের শীতে আশ্রয় না পেলে শীতেই অক্কালাভ। দুই বন্ধু কলোন গির্জের মা-মেরিকে স্মরণ করে এক ডজন মোমবাতি মানত করলে। আপনি তো মুসলমান, এসব মানেন না, কিন্তু–’
আমি বললুম, আলবত মানি। একশবার মানি। কলকাতায় মৌলা আলীর দৰ্গায় মোমবাতি মানত করলে বহু বাসনা পূর্ণ হয়। আর আমাদের দেশে এমন জায়গাও আছে যেখানে মানত করলে মোকদ্দমা পর্যন্ত জেতা যায়।’
ফ্রানৎসিস্কা শুধালেন, ‘ডিভোর্স পাবার দরগা আছে?’
আমি বললুম, বিলক্ষণ, তবে সেখানে স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে গিয়ে কামনোটা জানাতে হয়।’
নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘থ্যাঙ্ক ইউ’ তারপর গল্পের খেই তুলে নিয়ে বললেন, ‘কলোনের মা-মেরি বড় জাগ্ৰত দেবতা। একটা হোটেলে শেষটায় একটা ডবল রুম জুটে গেল, কিন্তু ব্যবস্থাটা শুনে দুই ইয়ারই আঁতকে উঠলেন।
‘ঘর পঞ্চাশ তলায়, আর লিফট্ৰ বিগড়ে গিয়েছে!
‘দুইজনই একসঙ্গে বললে, ‘হে মা-মেরি, এতটা দয়াই যখন করলে, তখন লিফট্টা সারাতে পারলে না মা?’
আমি বললুম, ‘আমাদের গোপালভাড়াও তাই বলেছিল,–
’এত দয়াই যদি করলি, মা কালী,
তবে আরেকটু দয়া করে,
বনে আছে দেদার ফড়িং
খা না দুটো ধরে।’
নয়রাট বললেন, ‘গল্পটা কি?’
আমি বললুম, ‘আপনাকে একদিন সময়মত আমাদের ‘গোপালভাঁড়-সাইক্ল’ শোনাব, তার অনেকগুলি ফ্রানৎসিস্কার সামনে বলা চলবে না।
নয়রাট বললেন, ‘তবে নিয়ে চলুন আপনাদের ডিভোর্স-দর্গায়।’
সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফ্রানৎসিস্কা ভাড়ারঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি বললুম, ‘অত তাড়া কিসের? ভারত যাবার জাহাজ আরো সপ্তাহখানেক পর ছাড়ে।’
নয়রাট বললেন, ‘তখন ট্যুনিস শেলকে বললে, ‘ভাই, এ ছাড়া আর উপায় যখন নেই তখন চ্য, সিঁড়ি ভাঙি আর কি?’
‘শেল বললে, ‘একটা ব্যবস্থা করলে হয় না, প্রতি তলা উঠতে উঠতে তুই এক-একটা করে গল্প বলবি আর তাতেই মশগুল হয়ে আমরা পঞ্চাশতলা বেয়ে নেব। তুই তো মেলা গল্প জানিস।’
ট্যুনিস বললে, ‘যা বলেছিস, সাধে কি আর তোকে সঙ্গে এনেছিলুম? তবে শোন,’ বলে আরম্ভ করলে সিঁড়ি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গল্প-বলা।’
নয়রাট বললেন, ‘সে কত বাহারে গল্প! আমি গল্প কলেকটু করি নে, কিন্তু আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে আমি আপনাকে আলাপ করিয়ে দেব, তিনি সব কটা জানেন।
‘তা সে কথা থাক।’
ট্যুনিস আর শেল এক এক তলার সিঁড়ি ভাঙে আর ট্যুনিস এক-একখানা জান–তর-র-র গল্প ছাড়ে। হেসেখেলে বিন-মেহন্নত, বিনা-কসরতে তারা পাঁচশতলা এক ঝটিকায় মেরে দিলে।
তখন ট্যুনিস বললে, ‘ভাই শেল, আমার সব গল্প খতম। আর কোন গল্প মনে পড়ছে না।’
‘তখন শেল বললে, ঘাবড়াস নি। আমারো কিছু পুঁজি আছে।’
বলে তখন শেল আরম্ভ করল গল্প বলতে। সেও কিছু কম বাহারে নয়, তবে ট্যুনিস তালেবর ব্যক্তি, তার সঙ্গে তুলনা হয় না।
‘করে করে তারা আরো চব্বিশখানার সিঁড়ি ভাঙলে-গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে।’
‘মাত্র একতলা বাকি। শেল দুম করে মাটিতে বসে পড়ল। এক ঝটিকায় হোক আর উনপঞ্চাশ ঝটিকায়ই হোক পা-গুলো তো আর গল্প শুনতে পায় না। শেল ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ে বললে, ‘ভাই আমার গুদোমও খতম।’
‘তখন টুনিশ বললে, ‘কুছ পরোয়া নদীরদ। আমার একখানা গল্প মনে পড়েছে— একদম সত্যি গল্প। —আমরা ফ্রাটের চাবি সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি।’
***
লঞ্চ খেতে এসে তখন প্ৰায় চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে অথচ গাল-গল্পের কম্বলের ভিতর এমনি ওম জমে গিয়েছে যে সে কম্বল ফুটো করে বেরতে ইচ্ছে করে না। শীতের দেশ তো-উভয়ার্থে শীতের দেশ, ইয়োরোপীয়দের মনেও শীত; আড্ডা জমিয়ে সঙ্গ-সুখের আলিঙ্গনে সেটাকে গরম করতে জানে না-তাই এদের কুণ্ডুলিতে বহুদিন পরে যেন বসন্ত রেস্টুরেন্টে’র আনন্দ পেলুম।
শেষটায় একটা হাফ-মোক পেয়ে বললুম, ‘আমি তা হলে উঠি।’
নয়রাটি একটি কথা বললেন, ‘কেন?’
আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। এরকম অবস্থায় সচরাচর বলা হয়, ‘সে কি কথা? এখনই যাবেন কেন?’ কিংবা ‘বড় কাজ পড়ে আছে বুঝি?’ অথবা অন্য কিছু। আমার কোনো জবাব যোগাল না।
নয়রাট বললেন, ‘দেখুন মশাই, আপনাকে বলি নি, কিন্তু আপনাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। গোল কয়েকদিন ধরে যখনই লেকের পাঁড় দিয়ে কাজকর্মে কোথাও যেতে হয়েছে, তখনই আপনাকে দেখেছি, ঐ একই বেঞ্চের উপর-তাও আবার একই পাশে-বাসে আছেন। শুনেছি, ইংলন্ডের পার্কে চেয়ারে বসলে তার জন্যে ট্যাক্স দিতে হয়—’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘সেখানে দম ফেলতেও ট্যাক্স দিতে হয় এবং তারই ভয়ে কেউ যদি দম বন্ধ করে, তবে মরে গিয়ে তাকে ডেথ ট্যাক্স দিতে হয়।’
নয়রাট বললেন, ‘তাহলে বিবেচনা করি সেখানে বিয়ের উপরও ট্যাক্স আছে। আহা, ইংলন্ডে জন্মালে হত।’
ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘আহা আমি যদি তিব্বতে জন্মাতুম। সেখোন প্রত্যেক রমণীর পাঁচটা করে স্বামী থাকে, আর সব কটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।’
আমি বললুম, ‘ষাট, ষাট (ইংরেজিতে tut-tut), ও রকম অলুক্ষণে কথা কইবেন না।’
সমস্বরে, ‘কেন?’
আমি বললুম, ‘তাহলে আসছে জন্মে পেটারকে জন্মাতে হবে ইংলন্ডে আর মাদাম ফ্রানৎসিস্কা (বলে তাঁর দিকে ‘বাও’ করে বললুম), আপনাকে জন্ম নিতে হবে তিব্বতে।’
দুজনাই কিচির-মিচির করে উঠলেন। তার থেকে যে প্রশ্ন ওতরালো তার মোটামুটি জিজ্ঞাসা, ‘আসছে জন্মে’ কথাটার মানে কি? আমরা তো মরে গিয়ে হয় স্বগে যাব, কিংবা নরকে, কিংবা কঙ্গুর হয়ে যাব, ‘আসছে জন্মে’ তার অর্থ কি?
আমি বললুম, ‘এই যে পেটার শুধালেন, আমি বেঞ্চিতে সর্বসময় বসে থাকি কেন? তার অর্থ আমি চলাফেরা, হাঁটাহাঁটি করি না কেন? সুইটুজারল্যান্ডে যদি ইংলিশ কায়দায় বেঞ্চিতে বসতে হত তাহলে ট্যাক্স দিয়ে দিয়ে আমি ফতুর হয়ে যৌতুম সেকথা আমি খুব ভালো করেই জানি কিন্তু চলাফেরা করলে আমাকে খেসারতি দিতে হবে অনেক বেশি।’
লাইন কোন দিকে চলেছে ফ্রানৎসিস্কা যেন তার খানিকটা আভাস পেয়েছেন বলে মনে হল। পেটার কিন্তু রাত-ভর হদিস না পেয়ে শুধালেন, ‘এর কোনো মানে হয় না। আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে কেন? ইংলন্ডের মতো বর্বর দেশেও ও— রকম ট্যাক্স নেই।’
আমি বললুম, ‘পরজন্মে মানুষ এ পৃথিবীতে আসে পূৰ্ব্বজন্মের কামনা নিয়ে। আমি সমস্ত দিন যতদূর সম্ভব চুপচাপ বসে থাকি যাতে করে ভগবান পরজন্মে আমাকে এমন জায়গায় বসান যেখানে আমাকে কোন কিছু না করতে হয়। আমি যদি হাঁটাহাঁটি করি, তবে ভগবান ভাববেন, আমি ঐ কর্মই পছন্দ করি, আর আমাকে এ জগতে পাঠাবেন পোস্টম্যান করে। তখন মারি আর কি, জলঝড়ে, বিষ্টিতুফানে এর বাড়ি ওর বাড়ি চিঠি-পাৰ্শল বয়ে বয়ে।’
ফ্রানৎসিস্কা শুধালেন, ‘আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি নে কিন্তু কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি। আপনি বলতে চান, মানুষ মরে গিয়ে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। সে কি করে হয়?’
জ্ঞানী পাঠক! অপরাধ নেবেন না। আপনি সেস্থলে থাকলে আমার অনেক পূর্বেই বুঝে যেতেন, ‘জন্মান্তরবাদ’ এরা জানে না এবং আপনি সেইটি বুঝতে পেরে তক্খুনি তার শাস্ত্রসম্মত সদুত্তর দিয়ে দিতেন। কিন্তু আমি তো পণ্ডিত নই, দেশ আমাকে আদর করে না, দেশ আমাকে খেতে-পরতে দেয় না, তাই তো আমি লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা হয়ে গিয়েছি বিদেশ, আমি অতশত বুঝতে পারব কি করে?
তদুপরি আরেক কথা আছে। আমি মুসলমানের ছেলে। ইসলাম জন্মান্তরবাদ মানে না; যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মক্কাবাসীরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতো। সেই যুগের একটি আরবী কবিতা এই সুবাদে মনে পড়ল।
কবিতাটির গীতিরস বাঙলাতে অনুবাদ করার মত বাঙলা-ভাষা-জ্ঞান আমার নেই কিন্তু কল্পনা-চতুর পাঠক হয়তো আমার অনুবাদের ত্রুটি-বিচূতি পেরিয়ে গিয়ে ঠিক তত্ত্বটি সমঝে যাবেন। মরুভূমির আরব বেদুইন প্রিয়াকে উদ্দেশ করে বলছে,
প্রিয়ে,
আরবভূমি মরুভূমি, নীরস কর্কশ
তোমার আমার প্রেমের সুধাশ্যামলিম-রস
কেউ বুঝতে পারল না।
তাই সর্বন্দেহমনহাদয় দিয়ে প্রার্থনা করি,
তুমি যেন এমন দেশে জন্মাও,–
–আসছে জন্মে–
কত শত শতাব্দীর পরে তা জানিনে,
যেখানে মানুষ জলে ডুবে আত্মহত্যা করার
আনন্দ অনায়াসে অনুভব করতে পারে।’
এর টীকা অনাবশ্যক। আরব দেশে হাঁটু-জলের বেশি গভীরতর কোনো প্রকার নদীপুকুর নেই। তাই কবি জন্মান্তরে সেই দেশের কামনা করেছেন যেখানে মানুষ জলে ডুবে চরম শান্তি পায়।
সে দেশ বাঙলা দেশ। চেরাপুঞ্জির দেশ, যেখানে সব চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। নদীনালা, পুকুর-হাওরে জলের থৈ থৈ।
আরব বেদুইন কবি এই দেশই মনে মনে কামনা করেছিল।
***
আমি বললুম, ‘আসছে জন্মের কথা থাক। আপনি যে এ জন্মের কাহিনী আরম্ভ করেছিলেন সেইটি তো শেষ করলেন না। আপনি বলছিলেন আপনার গুটিকয়েক শখ পূরণ করার জন্য আপনি এক-টানা ছাব্বিশ বছর খেটে পয়সা জমিয়ে এখন দিব্য আরাম করতে পারছেন। আপনার শখগুলো কি?’
নয়রাট বললেন, ‘এক নম্বর দাবা-খেলা আর দু নম্বর-বলতে একটু বাধোবাধো ঠেকছে।’
আমি বললুম, ‘এইবার আপনারা ভদ্রতা ‘আরম্ভ’ করলেন।’
নয়রাট বললেন, ‘ভদ্রতায় ঠেকছে না। ঠেকছে। অন্য জায়গায়। তবু না হয় বলেই ফেলি। আমি যখন ইস্কুল যৌতুম তখন একটি জারজ ছেলেকে আমার ক্লাসের ছেলেরা বড় ক্ষ্যাপাত—ছেলেরা এ বিষয়ে যে কী রকম ক্রুর আর নিষ্ঠুর হতে পারে তার বর্ণনা আপনি নিশ্চয়ই মোপাসায় পড়েছেন। আমি তখনো গল্পটি পড়ি নি। কিন্তু আজ মনে হয় ছেলেটির দুৰ্দৈব কাহিনী মোপাসঁ শতাংশের একাংশও বর্ণনা করতে পারেন নি। আমার নিজের বিশ্বাস যৌনবোধ না জন্মানো পর্যন্ত মানুষের মনে স্নেহ করুণা ইত্যাদি কোনো প্রকারের সদগুণ দেখা দেয় না। তাই বালকেরা হয়। সচরাচর অত্যন্ত নিষ্ঠুর–আমি ক্লাসের আর সকলের চেয়ে ছিলুম বয়সে একটু বড়, আমার তখন নিজের অজানাতেই যৌনবোধ আরম্ভ হয়েছে এবং তাই ঐ হতভাগ্য ছেলেটার জন্য আমার হৃদয়ে গভীর বেদনার উদ্ৰেক হত। কিন্তু বয়সে বড় হলে কি হয়, আমি ছিলুম। একে রোগাপটকা, তার উপর মারামারি হাতাহাতির প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা। তাই আমি তাকে কোনো প্রকারে সাহায্য না করতে পেরে মনে মনে বড় লজ্জা বোধ করাতুম। তবে সুযোগ পেলেই, আর পাঁচটা ছেলের চোখে আড়ালে ওর হাতে একটা চকোলেট দিতুম, রাস্তায় দেখা হলে একটা আইসক্ৰীিম খাইয়ে দিতুম!
‘প্রথম যে-দিন তাকে চকলেট দিয়েছিলুম সেদিন সে আমার দিকে বদ্ধ ইডিয়াটের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল, তারপর দরব্দর করে তার দু চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল। ক্লাসের তিরিশটি কসাইয়ের ভিতরেও যে একটি ছেলে গোপনে গোপনে তার জন্য হৃদয়ে দরদ ধরে এর কল্পনাও যে কখনো তার মনের কোণে ঠাই দিতে পারে নি।’
তাকিয়ে দেখি ফ্রানৎসিস্কার চোখ ছলছল করছে। অথচ তিনি নিশ্চয়ই এ-কাহিনী আগে শুনে থাকবেন। মনে মনে বললুম, নয়রাট সত্যই সহধর্মিণী’ পেয়েছেন। বাইরে বললুম, ‘থামলেন কেন?’
বললেন, ‘এখনো বাধো-বাধো ঠেকছে। তবু বলছি, কারণ এ বিষয়ে আমি মিশনারি।’
‘ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললুম, ‘এই ফুল! চোখ মুছে ফেল। আর সবাই দেখে ফেললে তোকে জ্বালাবে আরো বেশি, আমাকেও রেহাই দেবে না।’
‘চোখের জলের সঙ্গে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা মিশে গিয়ে তার চেহারা যে কি রকম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তার ছবি আমি আজো দেখতে পাই।
‘আপনাকে কি বলবো, তারপর সেদিন ক্লাসে বসে যখনই আড়নয়নে তাকিয়েছি তখনই দেখেছি, সে চোখ বন্ধ করে আছে, তার ঠোঁটের কোণে গভীর প্রশস্তির মৃদু হাস্য, আর গালের আপেল দুটো খুশিতে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো যেন চেপে ধরেছে। আমি তো ভয়ে মরি, মুখটা আবার কি বলতে গিয়ে কি না বলে ফেলে।
‘তার পর দিন থেকে আরম্ভ হল আরকে আজব কেচ্ছা। ছেলেরা রুটিনমাফিক তাকে ‘ব্যা-ড’ বললে, চুলে ধরে টান দিলে, অন্যান্য প্রকরণেরও কোনো খাঁকতি হল না। কিন্তু সেও রুটিনমাফিক চিৎকার চেচামেচি গালাগাল দিলে না-সে দেখি, চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে হাসছে—আমি ভাবলুম, হয়েছে, ছোঁড়াটা বোধ করি ক্ষেপে গেছে।
‘বহু পরে সে আমাকে একদিন বলেছিল, এ নাকি তখন খুশিতে ডগোমগো, তার নাকি ভারী আনন্দ, তার আর কি ভয়, এই ক্লাসেই তার একটি বন্ধু রয়েছে, সে তাকে চকলেট খাইয়েছে।’
আমি বললুম, ‘অতিশয় হক কথা! ফার্সীতে প্রবাদ আছে—
‘দুশমন্ চি কুনদ্, আগর, মেহেরবান বাশাদ দোস্ত!’
“দুশ্মন কি করতে পারে, দোস্ত যদি মেহেরবান্ হয়!”’
নয়রাট উল্লসিত হয়ে ফ্রানৎসিসককে বললেন, ‘বউ, প্রবাদটা টুকে নাও তো, কাউকে দিয়ে পাসীতে লিখিয়ে নিজে জর্মনে গথিক হরফে তর্জমা লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবো।’
আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘এতদিন ধরে আমি জুতসই একটা প্রবাদের সন্ধানে ছিলুম-আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।’
তারপর বললেন, ‘ছোঁড়াটা অদ্ভুত। আমাকে বিপদে না ফেলার জন্য আমার কাছে এসে ন্যাওটামি করতো না। একলা-একিলি দেখা হলে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি মুচকি হেসে চোখ বন্ধ করত।
‘তার কয়েকদিন পরে আমার জন্মদিন। ক্লাসের ছোঁড়াগুলোর প্রতি যদিও আমি ঐ ছোকরাটাকে জ্বালাতন করার জন্য বিরক্ত হাতুম। তবু অন্য বাবদে ওরাই তো আমার সঙ্গী; তাই তাদের নেমন্তন্ন করলুম, আর না করলে মা-ই বা কী ভাববে? তারা আমার জন্য উপহার আনলে বই, পেন্সিল, চুরি, কলের লাটিম এবং আর পাঁচটা জিনিস। আমরা কেক লেমনেড খাচ্ছি, জোর হৈ-হুল্লোড় চলছে, এমন সময় বাড়ির দাসী আমার কানে কানে বললে, ‘ছোটবাবু, তোমার জন্য একটি ছেলে নিচের তলায় পেটে দাঁড়িয়ে। কিছুতেই উপরে আসতে চায় না; তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।’
‘আমার সব বন্ধুই তো গটগট করে উপরে আসে। এ আবার কে?
‘গিয়ে দেখি সেই পাগলা। হাতে এক ঢাউস বাক্স। লাজায় লাল হয়ে বললে’–তোর জন্মদিনে একটা প্রেজেন্ট এনেছি। ছোট্ট একটা পাল-লাগানো ইয়ট।’
‘বলে কি? ‘ইয়ট’ তখন আমাদের স্বপ্নের বাইরে। পুরো বছরের জলখাবারের পয়সা জমালেও আমাদের ক্লাসের ধনী ছোকরা আডলফ পর্যন্ত ইয়ট’ কিনতে পারে না—তখনো জানতুম না, সে পয়সাওলা ছেলে।
‘লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। বললুম, ‘তুই উপরে চ, কেক খাবি।’
‘বললে, ‘না, ভাই, তুই যা, উপরে আরো অনেক সব রয়েছে।’’
‘আমি তাকে জোর করে উপরে টেনে নিয়ে এলুম। কোখোকে সাহস পেলুম আজো জানি নে। বোধ হয় ইয়টের কৃতজ্ঞতায়।’
আমি থাকতে না পেরে বললুম, ‘ছিঃ’, জিনিস নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।’
নয়রাট বললেন, ‘থ্যাঙ্ক ইউ। তার পর উপরে কি হল ঠিক বলতে পারব না। প্রথমটায় সবাই থ মেরে গেল। তারপর একে একে সক্কিলেই পাগলার সঙ্গে শেক-হ্যান্ড করলে। তার চোখ দিয়ে আবার সেই পয়লা দিনের মতো ঝরঝর করে জল নেমে এল।
‘সেই দিনই আমি মনস্থির করলুম, বড় হলে আমি সর্বত্র এরকম ছেলেদের অন্যায় অত্যাচার থেকে বাঁচাবো। ভগবান আমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন, এ শক্তি আমার ভিতর আছে।’
নয়রাট হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, ‘এখখুনি আসছি; আমি একটা টেলিফোন করতে ভুলে গিয়েছিলুম।’
বুঝলুম, বিনয়ী লোক, লজ্জা ঢাকবার অবকাশ খুঁজছেন।
—————–
(১) শব্দটা গ্ৰাম্য; কিন্তু পূজনীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিধানে শব্দটিকে অবহেলা করেন নি বলে আমি ড্যাস দিয়ে সারলুম। তিনি গুরুজন—ৰ্তার শাস্ত্ৰাধিকার আছে।
(২) ‘নেমকহারাম’ অর্থাৎ ‘অকৃতজ্ঞ, সমাসটা বাংলায় চলে। ‘নেমকহালাল’ ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ ‘কৃতজ্ঞ’। ‘নেমকহারাম’ ‘নেমকহালাল’ কথাগুলা কিন্তু ‘কৃতজ্ঞ’ ‘অকৃতজ্ঞের চেয়ে জোরদার। নিমক’ = ‘নুন’-তার অপমান’ (হারাম) কিম্বা সম্মান’ (হালাল)।
(৩) পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য
(৪) সুফীরা মদ্য ‘ভগবদ-প্রেম’ অর্থে ব্যাখ্যা করেন।
(৫) ‘রুবাই’ একবচন, ‘রুবাইয়াৎ’ বহুবচন।
পরিমল রায়
পরিমল রায়ের অকালমৃত্যুতে কেউ সখা, কেউ গুরু, কেউ সহকর্মী, কেউ প্রতিবেশী এবং দিল্লি শহর একটি উৎকৃষ্ট নাগরিক থেকে বঞ্চিত হল।(১) মৃত্যুকালে পরিমল রায় নিউইয়র্কে ছিলেন। কিন্তু এ আশা সকলেই মনে মনে পোষণ করতেন যে আমেরিকায় বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি আবার দিল্লিতেই ফিরে আসবেন এবং তার বন্ধুবান্ধব, তার শিষ্যমণ্ডলী তথা বাংলা সাহিত্যুমোদীজন তাঁর সে অভিজ্ঞতার ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন।
পরিমল রায় সত্যই নানা গুণের আধার ছিলেন।
একদা ‘মৌলানা খাকী খান’ আমাকে একটি ক্ষুদ্র বিতর্ক-সভাতে নিয়ে যান। সে সভাতে পরিমল রায় ভারতবর্ষে কি প্রকারে কলকব্জা কারখানা ফ্যাক্টরি তৈরি করার জন্য পুঁজি সংগ্ৰহ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরকম আলোচনা আমি জীবনে কমই শুনেছি। পরিমল রায় জানতেন, তার শ্রোতারা অর্থনীতি বাবদে এক একটি আস্ত বিদ্যাসাগর’; তাই তিনি এমন সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় মূল বক্তব্যটি বলে গেলেন যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সে পণ্ডিত্যকে অজ্ঞজনের সামনে নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ দৈনন্দিন সত্যরূপে প্রকাশ করার লৌকিক পদ্ধতি দেখে আমি মুগ্ধ হলুম। তাঁর ভাষণ শেষ হলে আমি দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলুম। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বাঘা পণ্ডিতের মত খেঁকিয়ে উঠলেন না। অতিশয় সবিনয়ে তিনি আমার দ্বিধাগুলোকে এক লহমায় সরিয়ে দিলেন। আমার আর শ্রদ্ধার অন্ত রইল না। পণ্ডিতজনের বিনয় মুখের চিত্তজয় করতে সদাই সক্ষম।
সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপচারি হয় নি। তার কয়েকদিন পরে আর এক সভাতে তার সঙ্গে দেখা। সুধালেন, ‘চিনতে পারছেন কি?’
আমি বললুম, ‘বিলক্ষণ।’ আর সঙ্গে সঙ্গে গড় গড় করে তার ভাষণের আটটি পয়েন্ট একটার পর একটা আউড়ে গেলুম। এ আমার স্মৃতিশক্তির বাহাদুরি নয়। এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ পরিমল রায়ের। পূর্বেই নিবেদন করেছি, পরিমল রায় তাঁর বক্তব্য এমন চমৎকার গুছিয়ে বলতে পারতেন যে, একবার শুনলে সেটি ভুলে যাওয়ার উপায় ছিল না। আজ যে বিশেষ করে পরিমল রায়ের শিষ্যেরাই সবচেয়ে বেশি শোকাতুর হয়েছেন, সেটা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।
কিন্তু এসব কথা থাক। অর্থনীতিতে পরিমল রায়ের পাণ্ডিত্য যাচাই করার শাস্ত্ৰাধিকার আমার নেই।
নিছক সাহিত্যিকের চেয়ে যারা আর পাঁচটা কাজে জড়িত থেকেও সাহিত্য চর্চা করেন, তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি বড়ই উল্লসিত হই। পেটের ধান্দার একটা হেস্তনেস্ত কোনো গতিকে করে নেওয়ার পর যে লোক তখনো বাণীকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি পেশাদারী সাহিত্যসেবীর চেয়েও শ্রদ্ধার পাত্র। পরিমল রায়ের কর্তব্যবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল বলে তার বেশি সময় কাটত অধ্যাপন অধ্যয়নে। তারপর যেটুকু সময় বাঁচিত তাই দিয়ে তিনি বাণীর সেবা করতেন।
এবং সকলেই জানেন সাহিত্যিকদের দুটি মহৎ গুণ তাঁর ছিল। তাঁর পঞ্চেন্দ্ৰিয় রসের সন্ধানে অহরহ সচেতন থাকত এবং তিনি সে রস বড় প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরে দিতে পারতেন। পরিমল রায়ের চোখে পড়ত দুনিয়ার যত সব উদ্ভট ঘটনা, আর সে সব উদ্ভট ঘটনাকে অতিশয় সাদামাটা পদ্ধতিতে বর্ণনা করার অসাধারণ ক্ষমতা তেমনি পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিলেন।
এদেশের লোকের একটা অদ্ভুত ভুল ধারণা আছে যে, রসিক লোক ভাড়ের শামিল। এ ভুল ধারণা ভাঙাবার জন্যই যেন পরিমল রায় বাঙলা দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। সকলেই জানেন, তিনি কথা বলতেন কম, আর তাঁর প্রকৃতি ছিল গম্ভীর—একটুখানি রাশভারি বললেও হয়তো বলা ভুল হয় না। চপলতা না করেও যে মানুষ সুরসিক হতে পারে পরিমল রায় ছিলেন। তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ; আমাদের নমস্য ‘পরশুরাম’ এস্থলে পরিমল রায়ের অগ্ৰজ।
আর যে গুণের জন্য পরিমল রায়কে আমি মনে মনে ধন্য বলতুম সেটা তাঁর লেখনী সংযম। এ গুণটি বাংলা দেশে বিরল। ভ্যাজর ভ্যাজার করে পাতার পর পাতা ভর্তি না করে আমরা সামান্যতম। বক্তব্য নিবেদন করতে পারি না। সংক্ষেপে বলার কায়দা রপ্ত করা যে কি কঠিন কর্ম সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম। এ গুণ আয়ত্ত করার জন্য বহু বৎসর ধরে অক্লাস্ত পরিশ্রম করতে হয়। তিন লাইনে যে নন্দলাল একখানা হাসিমুখ এঁকে দিতে পারেন। কিম্বা একটি মাত্র ‘সা’ দিয়ে আরম্ভ করেই যে ওস্তাদ শ্রোতাকে রসাধুত করতে পারেন তার পশ্চাতে যে কত বৎসরের মেহন্নত আর হয়রানি আছে সে কি দর্শক, শ্রোতা বুঝতে পারে?
তাই আমার শোকের অন্ত নেই যে, বহুদিনের তপস্যার ফলে যখন পরিমল রায়ের আপন সংক্ষিপ্ত নিরলঙ্কার ভাষাটি শান দেওয়া তলওয়ারের মত তৈরি হল, যখন আমরা সবাই এক গলায় বললুম, ‘ওস্তাদ, এইবারে খেল দেখাও’, ঠিক তখন তিনি তলওয়ারখানা ফেলে দিয়ে অস্তধান করলেন।
এই তো সেদিনকার লেখা। একটি মোটা লোক রায়েব বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ ঘোঁত ঘোঁত করে বেড়াতে বেরোন। আরেকটি রোগপটকা পনপন করে সেই সময় বেড়াতে বেরোয়। একজনের আশা ঘোঁতঘোঁতিয়ে রোগ হবে, আর একজনের বাসনা পািনপানিয়ে সে মোটা হবে। ফলং? যথা পূর্বম তথা পরম।
এ জিনিস চোখের সামনে নিত্যি নিত্যি হচ্ছে। কিন্তু কই, আমরা তো লক্ষ্য করি নি। পরিমল রায় এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করে এমনি কায়দায় সামনে তুলে ধরলেন যে, এখন রোগা মোটা যে কোন লোককে যখন ঘোঁত ঘোঁত কিম্বা পনপন করতে দেখি তখন আর হাসি সামলাতে পারি নে।
আমার বড় আশা ছিল পরিমল রায় দেশে ফিরে এসে মার্কিনদের নিয়ে হাসির হর্রা মজার বাজার গরম করে তুলবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, সুকুমার রায়, পরশুরাম এঁরা কেউ মার্কিন মুলুক যান নি। আশা ছিল পরিমল রায়ের মার্কিনবাস রসের বাজারে আসর জমাবে।
একটি আড়াই ছত্রের টেলিগ্রামে সব আশা চুরমার হল। কাকে সান্ত্বনা দিই? আমিই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি নে।
——-
(১) স্বর্গীয় পরিমল রায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতি জানাই।
প্ৰব্ৰজ্যা
রিয়োকোয়ানের বয়স যখন সতেরো তখন তার পিতা রাজধানীতে চলে যাওয়ায় তিনি গ্রামের প্রধান নির্বাচিত হলেন। তার দুই বৎসর পরে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করে সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
ধনজন সুখ-সমৃদ্ধি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই কেন যে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফিশার প্রচলিত কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করেছেন। কারো মতে রিয়োকোয়ানের কবিজনীসুলভ অথচ তত্ত্বান্বেষী মন জনপদপ্রমুখের দৈনন্দিন কূটনৈতিক কার্যকলাপে এতই ব্যথিত হত যে তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সঙ্ঘের শরণ নেন; কারো মতে ভোগ-বিলাসের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।
রিয়োকোয়ান নাকি এক সন্ধ্যায়। তার প্রণয়িনী এক গাইশা(১) তরুণীর বাড়িতে যান। এমনিতেই তিনি গাইশাদের কাছ থেকে প্রচুর খাতির-যত্ন পেতেন, তার উপর তখন তিনি গ্রামের প্রধান। গাইশা-তরুণীরা রিয়োকোয়ানকে খুশি করার জন্যে নাচল, গাইল-প্রচুর মদও খাওয়া হল। কিন্তু রিয়োকোয়ান কেন যে চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন তার কোন কারণ বোঝা গেল না। তার প্ৰিয়া গাইশা-তরুণী বার বার তার কাছে এসে তাঁকে আমোদ-আহ্বাদে যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না। তিনি মাথা নিচু করে আপনি ভাবনায় মগ্ন রইলেন।
প্রায় চারশ টাকা খরচ করে সে রাত্রে রিয়োকোয়ান বাড়ি ফিরলেন। পরদিন সকাল বেল রিয়োকোয়ান বাড়ির পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে বসলেন না। তখন সকলে তার ঘরে গিয়ে দেখে, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কি হয়েছে বোঝাবার জন্য যখন কম্বল সরানো হল তখন বেরিয়ে এল রিয়োকোয়ানের মুণ্ডিত মস্তক আর দেখা গেল তার সর্বাঙ্গ জাপানী শ্রমণের কালো জোব্বায় ঢাকা।
আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময় দূর করার জন্য রিয়োকোয়ান বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু একটুখানি হাসলেন!। তার পর বাড়ি ছেড়ে পাশের কহশহভী সঙ্ঘের (মন্দির) দিকে রওয়ানা হলেন। পথে তার বল্লভ গাইশার বাড়ি পড়ে। সে দেখে অবাক, রিয়োকোয়ান শ্রমণের কৃষ্ণবাস পরে চলে যাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে সে তাঁর জামা ধরে কেঁদে, অনুনয়-বিনয় করে। বলল, ‘প্রিয়, তুমি এ কি করেছি! তোমার গায়ে এ বেশ কেন?’
রিয়োকোয়ানেরও চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু তবু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি সঙ্ঘের দিকে এগিয়ে গেলেন।
হায়, অনন্তের আহ্বান যখন পৌঁছয় তখন সে ঝঞার সামনে গাইশা-প্ৰজাপতি ডানা মেলে কি বল্লভকে ঠেকাতে পারে?
ফিশার বলেন, এ-সব কিংবদন্তী তার মনঃপুত হয় না। তার মতে এগুলো থেকে রিয়োকোয়ানের বৈরাগ্যের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।
ফিশারের ধারণা, রিয়োকোয়ান প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে সন্ন্যাসের অনুপ্রেরণা পান। তিনি যে-জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন সে-জায়গায় প্রকৃতি গ্ৰীষ্ম বসন্তে যে-রকম মধুর শান্তভাব ধারণ করে ঠিক তেমনি শীতকালে ঝড়-ঝঞার রুদ্র রূপ নিয়ে আঘাত আবেগ দিয়ে জনপদবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফিশারের ধারণা-রিয়োকোয়ানের প্রকৃতিতে এই দুই প্রবৃত্তিই ছিল; এক দিকে ঋজু সান্ত পাইন-বনের মন্দ-মধুর গুঞ্জরণ, অন্য দিকে হিম ঋতুর ঝঞা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছাস।
প্রকৃতিতে এ দ্বন্দ্বের শেষ নেই—রিয়োকোয়ান তার জীবনের দ্বন্দ্ব সমাধানকল্পে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ফিশার দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা বলেন নি–এই তাঁর ধারণা।
মানুষ কেন যে সন্ন্যাস নেয়। তার সদুত্তর তো কেউ কখনো খুঁজে পায় নি। সন্ন্যাসী চক্রবতী তথাগত জরা-মৃত্যু দর্শনে নাকি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন; আরো তো লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন জরা-মৃত্যু চোখের সামনে দেখে, কিন্তু কই তারা তো সন্ন্যাস নেয় না? বার্ধক্যের ভয়ে তারা অর্থসঞ্চয় করে আরো বেশি, মৃত্যুর ভয়ে তারা বৈদ্যরাজের শরণ নেয় প্ৰাণপণে-ত্রিশরণের শরণ নেবার প্রয়োজন তো তারা অনুভব করে না। যে জরা-মৃত্যু বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাস এবং মুক্তি এনে দিল সেই জরা-মৃত্যুই সাধারণ জনকে অর্থের দাস এবং বৈদ্যের দাস করে তোলে।
গাইশা-তরুণীর প্রেমের নিম্মফলতা আর ক্ষণিকতা হািদয়ঙ্গম করে রিয়োকোয়ান সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? তাই বা কি করে হয়? প্রেমে হতাশ হলেই তো সাধারণ মানুষ বৈরাগ্য বরণ করে,-রিয়োকোয়ানের বেলা তো দেখতে পাই গাইশা-প্ৰণয়িনী তাকে করুষ কণ্ঠে প্ৰেমনিবেদন করে সন্ন্যাস-মার্গ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।
এবং অতি সামান্য কারণেও তো মানুষ সন্ন্যাস নেয়। কন-ফুৎসিয় কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তার কারণ ছন্দে বেঁধে দিয়েছেন :
মসৃণ দেহ উচ্চপৃষ্ঠ উদ্ধত বলীয়ান
বৃষ চলিয়াছে ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আগুয়ান
সে করিল এক ধেনুর কামনা অমনি শৃঙ্গাঘাত
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র; সংসারে। প্ৰণিপাত!
(-সত্যেন দত্ত)
এবং এ সব কারণের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কারণে মানুষ যে সন্ন্যাস নেয়। তার উদাহরণ তো আমরা বাঙালি জানি। ‘ওরে বেলা যে পড়ে এল’–অত্যন্ত সরল দৈনন্দিন অর্থে এক চাষা আর এক চাষাকে এই খবরটি যখন দিচ্ছিল তখন হঠাৎ কি করে এক জমিদারের কানে এই মামুলী কথা কয়টি গিয়ে পৌঁছল। শুনেছি, সে জমিদার নাকি অত্যাচারীও ছিলেন এবং এ-কয়টি কথা যে পূর্বে কখনো তিনি শোনেন নি সে-ও তো সম্ভবপর নয়। তবে কেন তিনি সেই মুহূর্তেই পালকি থেকে বেরিয়ে এক বস্ত্ৰে সংসার ত্যাগ করলেন?
সমুদ্রবক্ষে বারিবর্ষণ তো অহরহ হচ্ছে, শুক্তির অভাব নেই। কোটি কোটি বৃষ্টিবিন্দুর ভিতর কোনটি মুক্তায় পরিণত হবে কেউ তো বলতে পারে না, হয়ে যাওয়ার পরেও তো কেউ বলতে পারে না কোন শুক্তি কোন মুক্তায় মুক্তি পেল।
রাজার ডাকঘর আমলের জানালার সামনেই বসল কেন? অমলই বা রাজার চিঠি
পেল কেন?
শুধু পতঞ্জলি বলেছেন, ‘তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ’ (১, ২৯)। অর্থাৎ যাদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল তাঁরাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে মোক্ষ পান। কিন্তু কাদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল হয় আর কেনই বা প্রবল হয় তার সন্ধান পতঞ্জলি তো দেন নি।
তাই বোধ হয় শাস্ত্রকাররা এই রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ‘সন্ন্যাসের সময়-অসময় নেই। যে মুহূর্তে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়, সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।’
রিয়োকোয়ান উনিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।
এ-প্রসঙ্গে ফিশার বলেন, আপাতদৃষ্টিতে রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাস গ্রহণ স্বার্থপরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরবতী জীবনে তিনি জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার থেকে তাকে স্বার্থপর বলা চলে না।’
এই সামান্য কথাটিতেই ফিশার ধরা দিয়েছেন যে তিনি ইয়োরোপীয়। সন্ন্যাস গ্রহণ কোনো অবস্থাতেই স্বার্থপরতার চিহ্ন নয়। অন্তত ভারতবর্ষে নয়।
সর্বস্ব ত্যাগ করে শান্তির সন্ধানে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাদের সম্মুখে কি কি বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হতে পারে, তার বর্ণনা ভারতবর্ষের সাধকেরা দিয়ে গিয়েছেন। সংসার ত্যাগের প্রথম উত্তেজনায় মানুষ যে তখন সম্ভাব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখা টানতে পারে না, সে সাবধান-বাণী ভারতীয় গুরু বার বার সাধনার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এবং সব চেয়ে বেশি সাবধান করে দিয়ে গিয়েছেন উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে।
ভারতবর্ষ নানা দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে এই সব চরম সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছে বলেই পরবর্তী যুগের ভারতীয় সাধকের ধ্যান-মার্গ অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চীন জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধভূমি ভারতবর্ষের এ ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত নয়। তারা নিয়েছে আমাদের সাধনার ফল—আমাদের পন্থা যে কত পতন-অভু্যুদয় দ্বারা বিক্ষুব্ধ, তার সন্ধান ভারতবর্ষের বাইরে কম সাধকই পেয়েছেন। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভবের প্রত্যাশা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে বহু নবীন সাধক সাধনার দৃঢ় ভূমি থেকে বিচ্যুত হন।
রিয়োকোয়ানের জীবনী-লেখক অধ্যাপক ফিশারের বর্ণনা হতে তাই দেখতে পাই, তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করে কি অহেতুক কঠোর কৃচ্ছসাধনের ভিতর দিয়ে নির্বাণের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব যে সব আত্মনিপীড়ন বর্জনীয় বলে বার বার সাধককে সাবধান করে দিয়েছেন, বহু জাপানীসঙ্গে সেই আত্মনিপীড়নকেই নির্বাণ লাভের প্রশস্ততম পন্থা বলে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল।
ফিশার বলেন, ‘সঙ্ঘের চৈত্যগৃহে কুশাসনের উপর পদ্মাসনে বসে দেওয়ালের দিকে মুখ করে নবীন সাধককে প্রহরের পর প্রহর আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করতে হত। একমাত্র আহারের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়েই দেয়াল ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফেরাবার অনুমতি তাদের ছিল না। একটানা কুড়ি ঘণ্টা ধরে কখনো কখনো তাদের ধ্যানে নিমজ্জিত থাকতে হত এবং সেই ধ্যানে সামান্যতম বিচূতি হলে পিছন থেকে হঠাৎ স্কন্ধোপরি গুরুর নির্মম লগুড়াঘাত।’
ধ্যানে নিমজ্জিত হবার চেষ্টা যাঁরাই করেছেন, তারাই জানেন, প্রথম অবস্থায় নবীন সাধক ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। একেই বলে জড়-সাধনা এবং পতঞ্জলি তাই যে উপদেশ দিয়েছেন, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, অল্প সময়ে ফললাভের আশা করা সাধনার প্রতিকূল। অত্যধিক মানসিক কৃচ্ছসাধনের ফলে কত সাধক যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান, সে কথা ভারতীয় গুরু জানেন বলেই শিষ্যকে অতি সস্তপণে শারীরিক ও মানসিক উভয় সাধনাতে নিযুক্ত করে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হতে উপদেশ দেন।
আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, রিয়োকোয়ান সঙ্ঘের উৎকট কৃচ্ছসাধনায় ভেঙে পড়েন নি। নয়। বৎসর ধ্যান-ধারণার পর তার গুরুর মৃত্যু হয়। রিয়োকোয়ান তখন সঙ্ঘ ত্যাগ করে পর্যটকরূপে বাহির হয়ে যান। রিয়োকোয়ানের পরবতী জীবনযাপনের পদ্ধতি দেখলে স্পষ্ট অনুমান করা যায়, তিনি অত্যধিক কৃচ্ছসাধনের নিম্মফলতা ধরতে পেরেছিলেন বলেই সঙ্ঘ ত্যাগ করে পর্যটনে বাহির হয়ে যান।
দীর্ঘ কুড়ি বৎসর রিয়োকোয়ান ধ্যান-ধারণা ও পর্যটনে অতিবাহিত করেন। তাঁকে তখন কোন সব দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল, তার সন্ধান আমরা কিছুটা পাই তার কবিতা থেকে; কিন্তু সেগুলি থেকে রিয়োকোয়ানের সাধনার ইতিহাস কালানুক্রমিকভাবে লেখবার উপায় নেই।
কিন্তু একটি সত্য আমরা সহজেই তার কবিতা থেকে আবিষ্কার করতে পারি। দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি রিয়োকোয়ান কখনো পান নি। মাঝে মাঝে দু’একটি কবিতাতে অবশ্য রিয়োকোয়ানকে বলতে শুনি তিনি শাস্তির সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু পরীক্ষণেই দেখি, ভিন্ন কবিতায় তিনি হয় নব বসন্তের আগমনে উল্লসিত, নয় বৃষ্টি-বাদলের মাঝখানে দরিদ্র চাষার প্ৰাণাস্ত পরিশ্রম দেখে বেদনানুভূতিতে অবসন্ন। আমার মনে হয়, রিয়োকোয়ান যে চরম শাস্তি পান না, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য। নিৰ্দ্ধন্দ্ব জীবনের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের তো কবিতা রচনা করবার কোনো আবেগ থাকার কথা নয়। শান্ত রস এক প্রকারের রস হতেও পারে, কিন্তু সে রস থেকে কবিতা সৃজন হয় কি না তা তো জানিনে এবং হলেও সে রস আস্বাদন করবার মত স্পর্শকাতরতা আমাদের কোথায়? দক্ষিণাত্যের আলঙ্কারিকেরা তাই শঙ্করাবরণমকে সন্ন্যাস রাগ বলে সঙ্গীতে উচ্চস্থান দিতে সম্মত হন না। তাদের বক্তব্য সন্ন্যাসীর কোন অনুভূতি থাকতে পারে না, আর অনুভূতি না থাকলে রসসৃষ্টিও হতে পারে माँ!
রিয়োকোয়ানের কবিতা শঙ্করাবরণম বা সন্ন্যাসী রাগে রচিত হয় নি। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর সাধনা ও পর্যটনের পর যখন তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর পিতা জাপানের রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার জন্য আত্মহত্যা করেছেন তখন এক মুহূর্তেই তার সমস্ত সাধনা-ধন তাকে বর্জন করল।
খ্রিস্ট বলেছেন, ‘The foxes have holes and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.’ অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের জন্মভূমি নেই, জন্মভূমি নেই, আবাসভূমিও নেই। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে রিয়োকোয়ান বিচলিত হয়ে হঠাৎ যেন বাল্যজীবনে ফিরে গেলেন।
হেথায় হোথায় যেখানে যখন আমি
তন্দ্ৰামগন,-সুপ্তির কোলে আপনারে দিই ছাড়া
সেই পুরাতন নিত্য নবীর স্বপ্নের মায়া এসে
গুঞ্জরে কানে, চিত্ত আমার সেই ডাকে দেয় সাড়া।
এ স্বপ্ন নয়, ক্ষণেকের খেদ, উড়ে-যাওয়া আবছায়া
এ স্বপ্ন হানে আমার বক্ষে অহরহ একই ব্যথা
ছেলেবেলাকার স্নেহ ভালোবাসা, আমার বাড়ির কথা।
এ কি শ্রমণের বাণী, এ কি সন্ন্যাসের নিরাবলম্বতা!
ফিশার বলেন, ‘মাতৃভূমির আহ্বান রিয়োকোয়ানকে এতই বিচলিত করে ফেলল যে তিনি স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।’
অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সান্ত্বনা দেবার চেয়ে হয়ত সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যই তার হৃদয় তৃষাতুর হয়েছিল বেশি। আত্মজনের সঙ্গসুখ শ্রমণ রিয়োকোয়ান কখনো ভুলতে পারেন নি; সে-সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া ‘ক্ষণেকের খেদ’ নয়, চিত্তাকাশে ‘উড়ে-যাওয়া আবছায়া’ নয়, সে বেদনা অবচেতন মনে বাসা বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে নির্বাণ অন্বেষণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।
কিন্তু এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্যের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে কবি রিয়োকোয়ান শ্রমণ রিয়োকোয়ান হতে পারতেন না। কবি ও শ্রমণের মাঝখানে যে অক্ষয় সেতু রিয়োকোয়ান নির্মাণ করে গিয়েছেন, যে সেতু আমাদের কাছে চিরবিস্ময়ের বস্তু, সেই সেতুর বিশ্বকর্ম তিনি কখনই হতে পারতেন না।
ফিশার বলেন, কিন্তু বাড়ির কাছে পৌঁছে রিয়োকোয়ান থামকে দাঁড়ালেন, নিজের আচরণে লজ্জিত হলেন এবং চিত্তসংযম আয়ত্ত করে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্বিতীয় প্ৰব্ৰজ্যা গ্ৰহণ করলেন। ফিশার বলেন, বোধ হয় রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাসবৃত্তি তাঁর নীচাশক্তি থেকে প্রবলতর ছিল বলেই শেষ মুহূর্তে তিনি স্বগ্রামে প্রবেশ করলেন না। তাই হবে। কারণ, উপেন দুই বিঘে জমি কিছুতেই না ভুলতে পেরে শেষকালে যখন আপনি বাস্তুভিটায় ফিরে এল, তখন সে দুটি আমের লোভ সম্বরণ করতে পারল না। আর যে-চিত্ত সন্ন্যাসের দৃঢ় ভূমি নির্মাণে তৎপর সে-চিত্ত ক্ষণিক দুর্বলতার মোহে স্বগৃহে ফিরে এলেও গৃহসংসারের প্রকৃত রূপ হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ও প্রবাসের দূরত্বে যে গৃহ তার কাছে মধুময় বলে মনে হয়েছিল (নিকটে ধূসর-জর্জর অতি দূর হতে মনোলোভা) তার বিকট রূপ দেখে সে তখন পুনরায় ‘আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র সংসারে প্রণিপাত’ বলে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে।
বৌদ্ধ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন সন্ন্যাসধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে না। স্বয়ং বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর কপিলাবস্তুতে ফিরে এসেছিলেন। শ্রমণ রিয়োকোয়ান বোধিলাভ করতে পারেন নি বলেই স্বগ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।
এই সময় রিয়োকোয়ানের পিতার নিজের হাতের লেখা একটি কবিতা পুত্রের হাতে এসে পড়ে; কবিতাটি তিন লাইনে লেখা জাপানী হাক্কু পদ্ধতিতে রচিত :-
কি মধুর দেখি রেশমের গাছে ফুটিয়াছে ফুলগুলি;
কোমল পেলাব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা তুলি!
রিয়োকোয়ানের মৃত্যুর পর এই কবিতাটি পাওয়া গিয়েছে। আর এক প্রান্তে রিয়োকোয়ানের নিজের হাতে লেখা, ‘হায়, এই কুয়াশার ভিতর বাবা যদি থাকতেন! কুয়াশা সরে গেলে তো বাবাকে দেখতে পেতুম।’
বোধ হয়, এই সময়কারই লেখা আর একটি কবিতা থেকে রিয়োকোয়ানের মনের ংগ্রাম স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে :–
এই যে জীবন, এই যে মৃত্যু প্ৰভেদ কোথাও নাই,
যে জন জানিল তার কাছে বঁচা হয়ে ওঠে। মধুময়।
কিন্তু হায় রে মাটি দিয়ে গড়া অন্ধ আমার হিয়া
ফিরে চারি দিকে–রিপুর জঙ্কা যখন যেদিকে বয়।
দুর্বর রণ! তার মাঝখানে শিশু আমি, অসহায়
ধুকধুক বুকে বাজে ‘ভুল’ বাজে ঠিক’—
চরম সত্য স্মরণ ছাড়িয়া লুপ্ত হয়েছে হায়!
এই দ্বন্দ্বই তো চিরন্তন দ্বন্দ্ব। সর্বদেশের সর্বকালের বহুলোক এই দ্বন্দ্বের নিদারুণ বর্ণনা দিয়েছেন। সত্য দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আমার রিপু যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে— এই প্রতিবন্ধক ভিতরের না বাইরের, তাতে কিছুমাত্র আসে-যায় না, রাধার বেলা শাশুড়ি ননদী, হাফিজের বেলা,–
প্ৰেম নাই প্ৰিয় লাভ আশা করি মনে
হাফিজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।
এ দ্বন্দ্বের তুলনা দিয়েছেন সব কবিই আপনি হৃদয় দিয়ে। পূর্ববঙ্গের কবি হাসান রাজা চিঁড়ে-ভানার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছেন,-
হাসন জানের রূপটা দেখি ফাল্দি ফাল্দি উঠে
চিঁড়া-বারা হাসান রাজার বুকের মাঝে কুটে।
রিয়োকোয়ান কান পেতে বুকের ধুকধুকে শুনতে পেয়েছেন, ‘ভুল, ঠিক’, ‘ভুল, ঠিক’, ‘ভুল, ঠিক’!
এ তো গেল রিয়োকোয়ানের মনের দ্বন্দ্বের কথা, কিন্তু বাইরের দিকে রিয়োকোয়ানের জীবন অত্যন্ত সহজ গতিতেই চলেছিল। আহার শয়ন বাসস্থান সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন বলে সন্ন্যাস-আশ্রমের অভাব অনটন তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর ভ্ৰাম্যমান জীবন সম্বন্ধে জাপানে বহু গল্প প্রচলিত আছে এবং সে গল্পগুলির ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়, শ্রমণ রিয়োকোয়ান আর কিছু না হোক, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিলাসব্যসনের মোহ সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই গল্পগুলির কয়েকটি অনুবাদ করার পূর্বে বলে নেওয়া ভালো যে, বৃদ্ধ বয়সে রিয়োকোয়ান স্ব-গ্রামের দিকে ফিরে আসেন, আর পাশের পাহাড়ের এক পরিত্যক্ত আশ্রমে আশ্রয় গ্ৰহণ করেন। সেই জরাজীর্ণ গৃহে বহুকাল ধরে কেউ বসবাস করে নি, তার অর্ধেক ধ্বসে গিয়েছে, বাকিটুকু লতা-পাতার নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু ফিশার বলেন, বহু বৎসরের পরিভ্রমণে শ্ৰান্ত ক্লান্ত শ্রমণের কাছে এই ধ্বংসস্তুপই শাস্তিনীড় বলে মনে হল।
এই প্রত্যাবর্তন নিয়ে ফিশার দীর্ঘ আলোচনা করেন নি। আমাদেরও মনে হয়, করার কোনো প্রয়োজন নেই। গৃহী হোন আর সন্ন্যাসীই হোন, বার্ধক্যে আশ্রয়ের প্রয়োজন। রিয়োকোয়ানের বেলা শুধু এইটুকু দেখা যায় যে, সর্বসঙ্ঘের দ্বার তাঁর সামনে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি শ্রমণমণ্ডলীর প্রধান তো হতে চানই নি, এমন কি কারো সেবা পর্যন্ত গ্ৰহণ করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন।
রিয়োকোয়ানের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ পেয়ে তার ভাই-বোনেরা তাকে গৃহে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি।
বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে ফিরেছিলেন বটে, কিন্তু রাজপ্ৰসাদে আশ্রয় গ্ৰহণ করেন নি।
এই সময়ের লেখা একটি কবিতাতে রিয়োকোয়ানের শান্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় :–
এই তো পেয়েছি শান্তিনিলয়, খরতাপ হেথা নাই
জীবন-সাঁঝের শেষ ক’টি দিন কটাব হেথায় আমি
স্বপ্নের মোহে, কল্পনা বুনে। গাছেতে ছায়াতে হেথা
আমারে রাখিবে সোহাগে ঘিরিয়া-কাটাব দিবস-যামী।
———
(১) ‘গাইশ’ ঠিক বেশ্যা বা গণিকা নহে; মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা অথবা প্রাচীন গ্ৰীসের ‘হেটেরে’ শ্রেণীরা।
(২) জাতকের গল্পে আছে এক বৃদ্ধ শ্রমণ কোন সংঘে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইলে সেই সংঘের প্রধান শ্রমণ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। হয়তো জাতকের এই গল্পটি রিয়োকোয়ানের অজানা ছিল না, কারণ ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান বহু শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং জাতক বৌদ্ধধর্মের কতখানি স্থান অধিকার করেছে, সে কথা অমরাবতী, সাচীর ভাস্কর্যস্থাপত্য দেখলে আজও চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।
ফরাসী-জর্মন
গল্প শুনিয়াছি, এক পাগলা মার্কিন নাকি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্তী’ সম্বন্ধে যে সর্বাৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবে তাহাকে এক লক্ষ পীেভূ পারিতোষিক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়টি যে বৃহৎ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই; তাহা না হইলে মার্কিন বিশেষ করিয়া ঐ বিষয়টিই নির্বাচন করিবেন কেন?
সে যাহাই হউক, খবর শুনিবামাত্র ইংরাজ তৎক্ষণাৎ কুকের আপিসে ছুটি দিল। হরেক সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিয়া পক্ষাধিককাল যাইতে না যাইতেই সে আমাদের বনে উপস্থিত হইল ও বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই কেতাব লিখিল ‘আসামের পার্বত্যাঞ্চলে হস্তী শিকার’।
ফরাসী খবর শুনিয়া ধীরে সুস্থে চিড়িয়াখানার দিকে রওয়ানা হইল। হাতিঘর বা পিলখানার সম্মুখে একখানা চৌকি ভাড়া লইয়া আস্তে আস্তে শ্যাস্পেনে চুমুক দিতে লাগিল। আড়নয়নে হাতিগুলির দিকে তাকায় আর শার্টের কাফে নোট টুকে। তিন মাস পর চটি বই লিখিল ‘লামুর পারমি লেজেলেফা’ অর্থাৎ হিন্তীদের প্ৰেমরহস্য’।
জর্মন খবর পাইয়া না ছুটিল কুকের আপিসে, না গেল চিড়িয়াখানায়। লাইব্রেরিতে ঢুকিয়া বিস্তর পুস্তক একত্র করিয়া সাত বৎসর পর সাত ভলুমে একখানা বিরাট কেতাব প্রকাশ করিল; নাম ‘আইনে কুৎসে আইনকুরুঙ ইন ডাস সন্টুডিয়ম ডেস এলোফান্টেন’, অর্থাৎ হস্তীবিদ্যার সংক্ষিপ্ত অবতরণিকা’।
গল্পটি প্রাক-সভিয়েট যুগের। তখনকার দিনে রুশরা কিঞ্চিৎ দার্শনিক ভাবালু গোছের ছিল। রুশ খবর পাইয়া না গেল হিন্দুস্থান না। ছুটিল চিড়িয়াখানায়, না চুকিল লাইব্রেরিতে। এক বোতল ভদকা (প্রায় ‘ধান্যেশ্বরী’ জাতীয়) ও ত্রিশ বাণ্ডিল বিড়ি লইয়া ঘরে খিল দিল। এক সপ্তাহ পরে পুস্তক বাহির হইল, ভিয়েদিল লিলি ডি এলেফ্যান্ট’? তুমি কি কখনও হস্তী দেখিয়াছ? অর্থাৎ রুশ যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিয়া ছাড়িল যে হন্তী সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা শোনা যায় তাহা এতই অবিশ্বাস্য যে তাহা হইতে এমন বিরাট পশুর কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। অর্থাৎ হস্তীর অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অস্বীকার করিতে হয়।
আমেরিকান এইসব পন্থার একটিও যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সে বাজারে গিয়া অনেকগুলি হাতি কিনিল ও বক্রার্থে নয়, সত্য সত্যই ‘হাতি পুষিল’। কুড়ি বৎসর পরে তাহার পুস্তক বাহির হইল ‘বিগার এ্যান্ড বেটার এলেফেন্টস–হাউ টু গ্রো দেম?’ অর্থাৎ আরো ভালো ও আরও বৃহৎ হাতি কি করিয়া গজানো যায়।’ শুনিয়াছি আরো নানা জাতি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে হস্তীর স্বদেশবাসী এক ভারতবাসীও নাকি ছিলেন। কিন্তু ‘নেটিভ’ ‘কালা আদমী’ বলিয়া তাঁহার পুস্তিকা বরখাস্ত-বাতিল-মকুব-নামঞ্জুর-ডিসমিস-অসিদ্ধ করা হয়। অবশ্য কাগজে-কলমে বলা হইল যে, যেহেতুক ভারতবাসী হস্ত্রীকে বাল্যাবস্থা হইতে চিনে তাই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাকে পক্ষপাতদুষ্ট করিতে পারে!
গল্পটি শুনিয়া হস্তী সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না। সত্য, কিন্তু ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও মার্কিন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ঘোলাটে ধারণা তবুও হয়। সব জাতির বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ প্রাচ্য জাতিসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলে (আর ছাড়িতেই হইবে, কালা-ধলা একাসনে বসিতে পারে শুধু দাবার ছকেই) সত্যই বিদগ্ধ বলিতে বোঝায় জর্মন ও ফরাসীকে। বাদবাকি সকলেই ইহাদের অনুকরণ করে। তবে জর্মনরা নতমস্তকে স্বীকার করে যে কনসানস্ট্রেশন ক্যাম্পের’ অনুপ্রেরণা তাহারা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছিল। নিতান্ত তাহারা কোনো জিনিস অর্ধপক্ক রাখিতে চাহে না বলিয়াই এই প্রতিষ্ঠানটিকে পূৰ্ণ বৈদগ্ধ্যে পৌঁছাইয়াছিল।
জর্মন যদি কোনো ভারতবাসীকে পায়। তবে ইতি-উতি করিয়া যে কোনো প্রকারে তাহার সঙ্গে আলাপ জুড়িবার চেষ্টা করিবেই। আলাপ হওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া আপনাকে এক গেলাস বিয়ার দিবে, তারপর আপনার কালো চুলের প্রশংসা করিবে ও আপনার বাদামী (তা। আপনি যত ফর্সই হউন না কেন) অথবা কালো রঙের প্রশস্তি গাইবে। তারপর আপনাকে প্রশ্নবাণের শরশয্যায় শোয়াইয়া ছাড়িবে, আপনারা দেশে কি খান, কি পরেন, সাপের বিষে মানুষ কতক্ষণে মরে, সাধুরা শূন্যে উড়িতে পারেন কি না, কান্ট বড় না। শঙ্কর, তাজমহল নির্মাণ করিতে কত খরচ হইয়াছিল, অজন্তার কলা মারা গেল কেন, কামশাস্ত্রের প্রমাণিক সংস্করণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, সর্পপূজা এখনও ভারতবর্ষে চলে কি না, সাধারণ ভারতবাসীর গড়পড়তা কয়টি স্ত্রী থাকে, হিন্দু মুসলমান ঝগড়া কেন?’
‘কিন্তু হাঁ’, বার তিনেক মাথা নাড়াইয়া বলিবে, হ্যাঁ, গান্ধী একটা লোক বটে। ওরকম লোক যীশুখ্রীষ্টের পরে আর হয় নাই (ইংরাজকে কী ব্যতিব্যস্তই না করিল)। গোলটেবিল বৈঠকের পর তাহার কথা ছিল বাইমার শহরে আসিবার। কিন্তু আসিলেন না : আমরা বড়ই হতাশ হইয়াছিলাম। সত্যই কি গান্ধী গ্যোটেকে এত ভক্তি করেন যে তামাম ইউরোপে ঐ একমাত্র বাইমারই তাহার মন কড়িল?’
ভারতবাসীর প্রতি সাধারণ জর্মনের ভক্তি অসীম ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের অন্ত নেই।
ফুটবল
‘পরশুরামে’র কেদার চাটুজ্যে মশাই দূর থেকে বিস্তর মেমসাহেব দেখেছিলেন; আমিও দুর থেকে বিস্তর সিনেমা স্টার, পলিটিশিয়ান আর ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছি। দেখে ওঁদের প্রতি ভক্তি হয়েছে এবং গদগদ হয়ে মনে মনে ওঁদের পেন্নাম জানিয়েছি।
তাই কি করে যে ইস্টবেঙ্গল’ ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং ম্যানেজার মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তার সঠিক ব্যাখ্যা আমি এখনো সমঝে উঠতে পারি নি। তবে শুনেছি। আমরা যে-রকম খাঁচার ভিতর সিংহ দেখে খুশি হই, সিংহাঁটাও নাকি আমাদের দিকে কৌতূহলের সঙ্গে তাকায়, তার বিশ্বাস মানুষকে নাকি জড়ো করা হয় নিছক তাকে আনন্দ দেবার জন্য, যেদিন লোকের সংখ্যা কম হয় সেদিন নাকি সিংহ রীতিমত মন-মরা হয়ে যায়। (আরো শুনেছি, একটা খাঁচার গোটকয়েক শিক ভেঙে যাওয়াতে গরিলা নাকি দস্তুরমত ভয় পেয়ে গিয়ে পেছন-ফিরে দাঁড়িয়েছিল—তার বিশ্বাস ছিল খাঁচাঁটার উদ্দেশ্য তাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য।)
তাই যখন ইস্টবেঙ্গলে’র গুটিকয়েক রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমার দিকে তাকালেন। তখন আমি খুশি হলুম। বইকি। তারপর তাঁদের মাধ্যমে আর সকলের সঙ্গেও মোলাকত হয়ে গেল। সব কটি চমৎকার ভদ্রসন্তান, বিনয়ী এবং নত্ৰ। আমি বরঞ্চ সদম্ভে তাদের শুনিয়ে দিলুম ছেলেবেলার ‘বী’ টিমের খেলাতে কি রকম কায়দাসে একখানা গোল লাগিয়ে দিয়েছিলুম, অবশ্য সেটা সুইসাইডু গোল ছিল।
কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাদের খেলা দেখতে যাবো কি না? বললুম, ফাইনালের দিন নিশ্চয়ই দেখতে যাবো। ম্যানেজার বললেন, তা হলে তো যে-করেই হোক ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে হবে-বিবেচনা করুন, একমাত্র নিতান্ত আমাকে খুশি করার জন্যই তাঁদের কি বিপুল আগ্ৰহ!
ফাইনালের দিন ম্যানেজার আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিলেন।
***
দিল্লিতে ফুটবলের কদর কম। খেলা আরম্ভ হওয়ার পনেরো মিনিট পূর্বে গিয়েও দিব্য সীট পাওয়া গেল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার এক চ্যালাকে–শিটিফিটি দেওয়ার জন্য। পরে দেখলুম, ও ওসব পারে না, সে জন্মেছে পশ্চিমে। বললুম, ‘আরো বাপু মুখে আঙুল পুরে যদি হুইসিলই না দিতে পারিস তবে ফুটবল খেলা দেখতে এসেছিস কেন? রবিঠাকুরের ‘ডাকঘর’ দেখতে গেলেই পারিস।’
খেলা দেখতে এসেছে বাঙালি-তাদের অধিকাংশ আবার পদ্মার ও-পারের–আর মিলিটারি; এই দুই সম্প্রদায়। মিলিটারি এসেছে গোর্খা টিমকে সাহস দেবার জন্য, আর আমরা কি করতে গিয়েছি সে-কথা তো আর খুলে বলতে হবে না। অবশ্য আমাদের ভিতর যে ‘মোহনবাগান’ কিংবা ‘কালীঘাট’ ফ্যান ছিলেন না, সে-কথা বলব না, তবে কলকাতা থেকে এত দূরে বিদেশে তারা তো আর গোর্থীদের পক্ষ নিতে পারেন না। ‘দোস্ত নীপ্ত, লেকিন দুশমন ই-দুশমন হস্ত’ অর্থাৎ ‘মিত্র নয়।’ তবে শক্রর শত্রু’। এই ফাঁসী প্ৰবাদ সর্বত্র খাটে না।
পিছনে দুই সর্দািরজী বড্ড ভ্যাচর ভ্যাচর করতে লাগল। ইস্টবেঙ্গল নাকি ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছে নিতান্ত লোকসে কপাল জোরে, ওরা নাকি বড্ড রাফ খেলে। সবুট গোখার সঙ্গে রাফ খেলবে ইস্টবেঙ্গল! আর পদে পদে নাকি অফ-সাইডু। ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে ধুঘা বসিয়ে দি কিন্তু তার বপুটা দেখে সাহস হল না।
***
খেলার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হল ইস্টবেঙ্গল নিশ্চয় জিতবে। দশ মিনিটের ভিতর গোখরা গোটাচারেক ফাউল করলে আর ইস্টবেঙ্গল গোটাতিনেক গোল দেবার মোক নির্মমভাবে মিস করলে। একবার তো বলটা গোল-বারের ভিতরে লেগে দুম করে পড়ে গেল গোল লাইনের উপর। গোলি সেটা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেললে। আমি দু’হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে বললুম, ‘হে মা কালী, বাবা মৌলা আলী, তোমাদের জোড়া পাঠা দেব, কিন্তু এরকম আস্কারা দিয়ে মস্কোরা কোরো না, মাইরি।’ বলেই মনে পড়ল ‘মাইরি’ কথাটা এসেছে ‘মেরি’ থেকে। থুড়ি থুড়ি বলে দুৰ্গা, দুৰ্গা, দুৰ্গতিনাশিনী’কে স্মরণ করলুম।
হাফ-টাইম হতে চলল গোল আর হয় না—এ কী গৰ্ব্ববাযস্তনা রে, বাবা। ওদিকে অবশ্য ফাউলের সংখ্যা কমে গিয়েছে—রেফারি দেখলুম বেজায় দাঁড় লোক। কেউ পাউল করলে তার কাছে ছুটে গিয়ে বেশ দুকথা শুনিয়েও দেয়। জীত রহো বেটা। ফাউলগুলো সামলাও, তারপর ইস্টবেঙ্গলকে ঠ্যাকাবে কেন্ডা।
নাঃ, হাফ-টাইম হয়ে গেল। খেলা তখনো আঁটকুড়ী–গোল হয় নি।
ওহে চানাচুর-বাদাম-ভাজা, এদিকে এসো তো, বাবা। না, থাক, শরবতই খাই। চোঁচাতে চোঁচাতে গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। চ্যালাই পয়সাটা দিলে; তা দেবে না? যখন হুইসিল দিতে জানে না। রেফারি। আর কবার হুইসিল বাজালে? সমস্তক্ষণ তো বাজালুম আমিই।
***
হাফ-টাইমের পর খেলাটা যদি দেখতেন! সপাসপ আরম্ভ হল পোলো দিয়ে রুই মাছ ধরার মত গোল মারা।
আমি তো খেলার রিপোর্টার নই, তাই কে যে কাকে পাস করলে, কে কখন প্যার্টন উইভ করলে, কে কজন দুশমনকে নাচালে লক্ষ্য করি নি, তবে এটা স্পষ্ট দেখলুম, বলাটাই যেন মনস্থির করে ফেলেছে, সবাইকে এড়িয়ে গোখার গোলে ঢুকবেই ঢুকবে। একে পাশ কাটিয়ে, ওর মাথার উপর দিয়ে, কখনো বা তিন কদম পেছিয়ে গিয়ে, কখনো বা কারো দু’পায়ের মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে বলটা হঠাৎ দেখি ধাই করে হাওয়ায় চড়ে গোখা গোলের সামনে! সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লম্ফ দিয়ে টনসিলে এসে আটকে গিয়েছেবিকৃতস্বরে বেরল ‘গো-অ-অ-ল!’ (‘রূপদর্শী’ দ্রষ্টব্য)।
ফুটবল ভাষায় একটি তীব্র ‘সট’–এর (‘Sot’-shot নয়) ফলে গোলটি হল।
পিছনের সর্দারাজী বললেন, ‘ইয়ে গোল বাচানা মুশকিল। নহী থা।’
আমি মনে মনে বললুম, ‘সাহিত্যে একে আমরা বলি, ‘মুখবন্ধ’। এরপর আরো গোটা দুই হলে তোমার মুখ বন্ধ হবে। লোকটা জোরালো না হলে—।’
***
এ সব ভাবাভাবির পূর্বেই আরেকখানা সরেস গোল হয়ে গিয়েছে। কেউ দেখল, কেউ না। একদম বেমালুম। তারই ধকল কাটাতে কাটাতে আরেকখানা, তিসরা অতিশয় মান-মনোহর গোল! সেটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ও গোল কেউ বঁচাতে পারত না। দশটা গোলি লাগিয়ে দিলেও না।
এবার ম্যানেজারকে অভিনন্দন জানানো যেতে পারে। উঠে গিয়ে তাকে জোর শ্যাকহ্যান্ড করলুম। ভারী খুশি। আমায় বললে, ‘প্ৰত্যেক গোলে আপনার রি-একশন লক্ষ্য করছিলাম। আমরা আমাদের কথা রেখেছি (অর্থাৎ ফাইন্যালে উঠেছি)। আর আপনিও আপনার কথা রেখেছেন (আমি কথা দিয়েছিলুম ওরা ফাইনালে জিতবেই)।’ তার সঙ্গী তো আমার হাতখানা কপালে ঠেকালে।
মোরগ যে রকম গটগট করে গোবরের টিবিতে ওঠে। আমি তেমনি আমার চেয়ারে ফিরে এলুম। ভাবখানা, তিনটে গোলই যেন নিতান্ত আমিই দিয়েছি।
তারপর শাঁ করে আরো একখানা। দশ-বারো মিনিটের ভিতর ধনাধন চারখানা আদি ও অকৃত্রিম, খাঁটি-নিৰ্ভেজাল গোল!
পিছনের সর্দারাজী চুপ।
চ্যালাকে বললুম, চলো বাড়ি যাই। খেলা কি করে জিততে হয়, হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলুম তো!’
রাত্রে সব খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে গেলুম। গিয়ে দেখি এক ঢাউস ট্রফি। সঙ্গে আরেকটা বাচ্চা। বললুম, ‘বাচ্চাটাই ভালো। বড়টা রাখা শক্ত (উভয়ার্থে)।’
ওদেরই বিস্তর নাইন-নাইন্টি পুড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম।
বন
পশ্চিম-জার্মনীর রাজধানী বনবাসী হতে চলেছেন শুনে পাঠক যেন বিচলিত না হন। এ ‘বনে’র উচ্চারণ ‘ঘরে’র মত। বাংলা উচ্চারণের অলিখিত আইন অনুযায়ী ‘ন’ অথবা ‘ণ’ পরে থাকিলে একমাত্রিক শব্দে ‘অ’–কারটি ‘ও’–কারে পরিণত হয়। যথা-মন , বনউচ্চারিত হয় মোন বোন-ইত্যাদি রূপে। কিন্তু এই জর্মন Bonn শব্দের উচ্চারণে ‘ব’য়ের স্বরবর্ণটি ঘরের অ-কারের মত উচ্চারিত হয়। তাই পরাধীন জর্মনী আজ বনে রাজধানী পেয়ে যেন ঘর পেয়েছে একথা অনায়াসে বলা যায়।
কাগজে বেরিয়েছে বনের লোকসংখ্যা এক লক্ষ। আমাদের দেশে যেমন বলা হয়, পাঁচ বৎসর লালন করবে, দশ বৎসর তাড়না করবে এবং ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের ন্যায় আচরণ করবে, জর্মনীতে ঠিক তেমনি আইন, কোনো শহরের লোকসংখ্যা যদি একলক্ষে পৌঁছে যায়। তবে তিনি সাবালক হয়ে গেলেন, তাকে তখন ‘গ্রোস-স্টান্টু’ বা বিরাট নগররূপে আদর-কদর করে বার্লিন মুনিক কলোন হামবুর্গের সঙ্গে একাসনে বসাতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন ইংরেজ কর্তাদের মতে বন বিরাট নগর এবং জর্মনীর রাজধানী তারা বিরাট নগরেই স্থাপনা করেছেন।
কিন্তু এই কেঁদে ককিয়ে টায়ে-টায়ে এক-লক্ষী শহরেই রাজধানী কেন করতে হল? আমি বন শহরে বহু কর্মক্লান্ত দিবস এবং ততোধিক বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছি। বনের হাড়হদ আমি বিলক্ষণ জানি। তার লোকসংখ্যা কি কৌশলে ১৯৩৮ সালে এক লক্ষ করা হয়েছিল সেও আমার অজানা নয়। একলক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে পাশের একখানা গ্রামকে আদমশুমারীর সময় আপন কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিল-যদিও সে গ্রামটি বনের উপকণ্ঠে অবস্থিত নয়, দুয়ের মাঝখানে বিস্তর যাব-গমের তেপান্তরী ক্ষেত।
আসল তত্ত্ব হচ্ছে বন রুশ সীমান্ত থেকে অনেক দূরে। মার্কিন ইংরেজ ধরে নিয়েছে আসছে লড়াই-এ জর্মনী রুশের বিরুদ্ধে লড়বে এবং তখন রাজধানী যদি রুশ সীমাস্তের কাছে থাকে, তবে তাতে মেলা অসুবিধা—প্যারিস ফ্রান্সের উত্তর সীমাস্তে থাকায় তাকে যেমন প্রতিবারেই মার খেতে হয়, বেড়ালের মত রাজধারনীর বাচ্চা নিয়ে কখনো লিয়োঁ কখনো ভিশিময় ঘুরে বেড়াতে হয়।
কিন্তু বনে রাজধানী নির্মাণে আরেকটি মারাত্মক তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে গেল। বেলজিয়াম যে রকম প্রতিবার জর্মনীকে ঠেকাতে গিয়ে বেধড়ক মার খেয়েছে, এবার জর্মনী রুশকে ঠেকাতে গিয়ে সেইরকম ধারাই মার খাবে। বার্লিন গেছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে, বনও বাঁচবে না।
কিন্তু থাক এসব রসকষহীন রাজনীতি চর্চা। বরঞ্চ এসো সহ্যদয় পাঠক, তোমাকে বনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।
এপারে বন, ওপারে সিবেন গেবিৰ্গে’ অর্থাৎ সপ্তশ্ৰীলাচল। মাঝখানে রাইন নদী। সে নদীর বুকের উপর দিয়ে জাহাজ চড়ার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক তামাম ইউরোপ আমেরিকা থেকে জড়ো হয়। নদীটি একে বেঁকে গিয়েছে, দুদিকে সমতল জমির উপর গম-যবের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ছবির মত ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট ছোট্ট ঘরবাড়ি, সমতল জমির পিছনে দু সারি পাহাড় নদীর সঙ্গে সঙ্গে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে-মেঘমাশ্লিষ্টসানুং।
আর বন শহরের ভিতরটাও বড় মনোরম। বার্লিনের মত চওড়া রাস্তা নেই, পাচতলা বাড়িও নেই। মোটরের গোক-গাঁকিও নেই। আছে কাশী আগ্রার মত ছোট ছোট গলিখুঁচি, ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি-ঘর-দোর, ঘুমস্ত কাফে, অর্ধ-জাগ্রত রেস্তোরাঁ। আর বিশাল বিরাটবিপুল কলেবর আধখানা শহর জুড়ে ভুবনবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই জর্মনীতে প্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয়। হেরমান য়াকোবি এখানেই অধ্যাপক ছিলেন। তার শিষ্য কিফেল এখনো সেখানে সংস্কৃত পড়ান। পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর মোটা কেতাবখানার তর্জমা ইংরেজিতে এখনো হয় নি। কিফেলের সতীর্থ অধ্যাপক লশ উপনিষদ নিয়ে বছর বিশেক ধরে পড়ে আছেন। তার সুহৃদ রুবেনসের শরীরে ঈষৎ ইহুদি রক্ত ছিল বলে তিনি জর্মনী ছাড়তে বাধ্য হন। উপস্থিত তিনি তুর্কীর আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ান। বহুকাল ধরে রামায়ণখানা কামড়ে ধরে পড়ে আছেন—প্রমাণিক পুস্তক লেখবার বাসনায়।*
আর রাইনের ওয়াইনের প্রশংসা করার দায় তো আমার উপর নয়। ফ্রান্সের বর্দো বাগেন্ডির সঙ্গে সে কঁধ মিলিয়ে চলে।
আমি যখন প্রথম দিন আমার অধ্যাপকের সঙ্গে লেখাপড়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলুম, তখন তিনি ভুরি-ডুরি খাঁটি তত্ত্বকথা বলার পর বললেনঃ
‘এখানে ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে, তরুণীরা সহৃদয়া এবং ওয়াইন সস্তা। বুঝতে পারছেন, আজ পর্যন্ত আমার কোনো শিষ্যেরই বদনাম হয় নি যে নিছক পড়াশুনো করে সে স্বাস্থ্যভঙ্গ করেছে। আপনিই বা কেন করতে যাবেন?’ রাজধানী ঠিক মোকামেই থানা গাড়লো!
—–
* হালে খবর পেয়েছি। তিনি রুশদেশে গিয়ে সেখান থেকে রামায়ণের প্রামাণিক পাঠ প্ৰকাশ করেছেন।
বর্বর জর্মন
ন্যুরিনবের্গের মকদ্দমা এগিয়ে চলেছে, চতুর্দিকে আটঘটি বেঁধে তরিবত করে তামাম দুনিয়ায় ঢাকঢোল বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওঃ, কী বাঁচনটাই না বেঁচে গেছে! এয়সা দুশমনের জাত যদি লড়াই জিতত, তা হলে তোমাদের দমটি পর্যন্ত ফেলতে দিত না। ভাগ্যিস আমরা ছিলাম, বাঁচিয়ে দিলাম।
বিলেতী কাগজগুলো যে দাপাদাপি করে, তাতে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু নেই। তারা মার খেয়েছে, এখন শুধুমার দিয়েই খুশি হবে না, হরেক রকমে দুশমনকে অপমান করবে, তাতে ডবল সুখ; সে-সব কথা সবাইকেইনিয়ে-বিনিয়ে শোনাবে, তাতে তেহই সুখ; তারপর দেশটার কলকব্জা অর্থাৎ তার জিগর-কলিজা, নাড়িভূড়ি বিনা ক্লোরফর্মে টেনে টেনে বের করে তাকে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেবে, বেলজেন কাকে বলে।
কিন্তু এ দেশের ইংরেজি কাগজগুলো যখন ফেউ লাগে, তখন আর বরদাস্ত হয় না। ছিলি তো বাবা যুদ্ধের বাজারে বেশ, না হয়। স্কচ না খেয়ে সোলান খেয়েছিস, না হয় এসপেরেগাস আরটিচোক খেতে পাস নি, না হয় তুলতুলে ফ্ল্যানেল আর নানা রকমের হ্যাট ও ক্যাপ পাস নি বলে সর্দি ও গর্মির ভয়ে একটুখানি পা সামলে চলেছিলি, তাই বলে যা বুঝিস নে, মালুম নেই, তা নিয়ে এত চেন্নাচেল্লি করিস কেন? টু পাইস তো করেছিস, সে কথাটা ভুলে যাস কেন, তাই নিয়ে দেশে যা, দুদিন ফুর্তি কর, যে জায়গা নাগাল পাস নে, সেখানে চুলকোতে যাস নি। কিন্তু শোনে কে! সেই জিগির-জার্মান বর্বর, ‘বশ’, ‘হান’।
পরশুদিন জর্মন বর্বরতার প্রমাণ পেলুম, পুরনো বইয়ের দোকানে—একখানা কেতাব, আজকালকার জলের চেয়েও সস্তা দরে কিনলাম। তার নামধাম
BENGASCHE ERZAEHLER / DER SEG DEFR SEELE / AUS DEM INDISCEHN / INS DEUTSCH UEEERTAGEN / VONIRENHAR)T WAGNER /
অর্থাৎ ‘বাঙালি কথক’। (Enzaehler ধাতুর অর্থ কাহিনী বলা) ‘আত্মার জয়, ভারতীয় ভাষা হইতে জর্মনে রাইনহার্ট ভাগনার কর্তৃক অনুদিত।’
চমৎকার লাল মলাটের উপর সোনালী লাইনে একটি অজন্তা ঢঙের সুন্দরী বাঁশি। বাজাচ্ছে। ছবিখানি এঁকেছেন, কেউ-কেটা নয়, স্বয়ং অধ্যাপক এডমুনডশেফার।
কেতাবখানা যত্রতত্র বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে না-এস্তেহার রয়েছে। ‘ব্যুশারফ্রয়েন্ডে’ সংঘের সভ্যরা কিনতে পাবেন। বর্বর জর্মন বটতলা ছাপিয়ে, পেঙ্গুইন বেচে পয়সা করতে চায় না, তার বিশ্বাস-দেশে যথেষ্ট সত্যিকারের রসিক পাঠক আছে, তারা সংঘের সদস্য হয়ে বাছা বাছা বই কিনবে। আর যদি তেমনটা নাই হয়, হল না, চুকে গেল-বাংলা কথা।
‘বাংলা কথা।’ ইচ্ছে করেই বললাম, কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভাগনার সাহেব খাসা বাংলা জানেন। প্রথম আলাপে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহাশয় কোন ভাষার অধ্যাপক?
বাংলার।
বাংলার? বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে?
আজ্ঞে।
ছাত্ৰ কটি?
গেল পাঁচবছরের হিসেব নিলে গড়পড়তা ৩/৫।
গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল। আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, সেখানে ফি ক্লাসে নিদেনপক্ষে দেড়শটা বোদর ঝামেলা লাগাত। আদর্শ ছিল-৩০০ আপিন ওয়ান প্রফেসারের। বললাম, ৩/৫ একটু কম নয়?
ভাগনার বিরক্ত হয়ে বললেন, রবিবাবুর লেখা পড়েন নি।–The rose which is single need not envy the thorns which are many?
উঠে গিয়ে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা রেকর্ডখানি লাগালেন। ভাব হয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে বললাম, কুল্লে ৩/৫-এর জন্যে একটা আস্ত প্রফেসার। জর্মনরা বর্বর।
অবতরণিকাটি ভাগনার সাহেব নিজেই লিখেছেন; আগাগোড়া তৰ্জমা করে দিলুম।
‘সঙ্কলনটি আরম্ভ স্বৰ্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গদ্য রচনাগুলোকে বাংলার (tschota gallpa (ছোট গল্প) বলা হয়। ছোট গল্পগুলোকে এক রকমের ছোটখাটো উপন্যাস বলা যেতে পারে; শুধু নায়ক-নায়িকার সংখ্যা কম। গল্পগুলোর কাঠামো পশ্চিম থেকে নেওয়া হয়েছে, ভিতরকার প্রাণবস্তু কিন্তু খাঁটি ভারতীয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় সমস্ত গল্পটার আবহাওয়া একটিমাত্র মূল সুরের চতুর্দিকে গড়া। কতকগুলো আবার গীতিরসে ভেজানো। আবার এও দেখা যায়, ভারতবাসীর ধর্ম তার আচার-ব্যবহারের সঙ্গে এমনই বাধা যে গল্পের বিকাশ ও সমস্যা সমাধান এমন সব কারণের উপর নির্ভর করে, যেগুলো পশ্চিমে নভোলে থাকে না। আশা-নিরাশার দোলাখাওয়া কাতর হৃদয় এই সব গল্প। কখনও বা ধর্মের কঠিন কঠোর আচারের সঙ্গে আঘাত খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, কখনও বা তার ছোট গণ্ডির ভিতর শান্তি খুঁজে পায়; সেই ধুকধুক হৃদয়ের কঠোর দুঃখ, চরম শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে গভীর অন্তদৃষ্টি দিয়ে। আন্দ্রেয়াস হয়েসলারের সঙ্গে আমরা সুর মিলিয়ে বলতে পারি, “মানুষের আত্মার ভাঁজে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি।“
‘ভারতীয়দের প্রেম বড় উদার, তাতে গণিকারও স্থান আছে। গণিকাদের কেউ কেউ আবার জন্মেছে বেশ্যার ঘরে, বদ খেয়ালে বেশ্যা হয় নি। গ্যেটের গণিকাকে ভগবান অবহেলা করেন নি, এদেরও হয়তো অবহেলা করবেন না।
সঙ্কলনটি সুখে-দুঃখের গল্পেই ভর্তি করা হয়েছে; হাস্যরসের গল্প নিতান্ত কম দেওয়া হয়েছে। তার কারণও আছে, দুঃখ-যন্ত্রণা সব দেশের সব মানুষেরই এক রকম, কিন্তু হাস্যরস প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। করুণ রসে মানুষ মানুষকে কাছে টানে, হাস্যরস আলাদা করে। তবু তিনটি হাস্যরসের গল্প দেওয়া হল; হয়তো পশ্চিম দেশবাসীরা সেগুলোতে আনন্দ পাবেন।
‘বিশ্বসাহিত্যের সেবা যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সব চেয়ে ভাল। রচনা বাদ দেওয়া অন্যায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া চলে না। তার ‘লিপিকা’ থেকে তাই কয়েকটি সব চেয়ে ভাল লিখন দেওয়া হল; এগুলোকে ছোট ছোট গল্প বলা ভুল হবে।।(১) লেখাগুলো সহজেই দুভাগে আলাদা করা যায়, কতকগুলো মহাকাব্যের কাঠামোয় গড়া বলে গভীর সত্যের রূপ প্রকাশ করে তোলে, আর কতকগুলো ছবির মত কিসের যেন প্রতীক, কেমন যেন অস্বচ্ছ অর্ধ-অবগুষ্ঠিত অনাদি অনন্তের আস্বাদ দেয়, অথবা যেন নিগূঢ় আত্মার অন্তনিহিত কোমল নিশ্বাস আমাদের সর্বাঙ্গে স্পর্শ দিয়ে যায়।
সর্বশেষ যাঁরা তাঁদের লেখার অনুবার করবার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে যাঁরা এই সঙ্কলনের গোড়াপত্তন ও সম্পূর্ণ করাতে সাহায্য করেছেন। সদুপদেশ দিয়েছেন ও অনুবাদে যাতে ভুলত্রুটি না থাকে তার জন্য আমি নিম্নলিখিত মহাশয়দের কাছে কৃতজ্ঞ,-হের দ. প. রায়চৌধুরী, ডি. ফিল. (গ্যোটিঙেন); ইঞ্জিনিয়র বিদ্যার্থী অ. ভাদুড়ী; য. চি. হুই, এম.এস-সি; যা ভবসু, ডি.ফিল, (বার্লিন) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাধারী স.চ. ভট্টাচার্য।(২) সুরসিক, বহু ভাষায় সুপণ্ডিত লাভ, রামস্বামী আইয়ার(৩) এম.এ.বি.এল. বেশির ভাগ মূল লেখাগুলি পাঠিয়েছেন ও সঙ্কলন আরম্ভ করার জন্য উৎসাহিত করে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য গৃহিণীকে ধন্যবাদ।(৪)
অবতরণিকাটি নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করা যায় কিন্তু আমার উদ্দেশ্য পাঠক যেন নিজেই ভাগনার সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। আমার শুধু একটি বক্তব্য যে অবতরণিকার ভাষ্যটি সরল, যাঁরা মূল জর্মনে কনট হেগেল এমন কি টমাস মানও পড়েছেন তারাই জানেন জর্মনে কি রকম আড়াইগজী সব বাক্য হয়। ভাগনারের জর্মন অনেকটা বাংলা ছন্দের—কিছুটা প্রমথ চৌধুরীর মত। বাক্যগুলো ছোট ছোট; সাদামাটা খাস জর্মন কথার ব্যবহার বেশি কিন্তু দরকারমত শক্ত লাতিন কথা লাগাতে সায়েব পিছপা হন নি। জর্মন গুরুচণ্ডালীর সম্বন্ধে বাংলার মত ভয়ঙ্কর সচেতন নয়। বাগনার আবার সাধারণ জর্মনের চেয়েও অবচেতন।
পাঠকের সব চেয়ে জানার কৌতূহল হবে যে, কার কার লেখা বাগনার সাহেব নিয়েছেন। তার ফিরিস্তি দিচ্ছি :–
১। আমার দেশ (কবিতা) : শ্ৰীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়(৪) (Schridvidschendralal Raj)
২। সন্ন্যাস : শ্ৰীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (বিম্বদল)
৩। অঙ্কিত; গোলাপ; চোর; কুসুম; শিউলি : শ্ৰীহেমেন্দ্ৰকুমার রায় (সিঁদুর চুপড়ি, মধুপর্ক)
৪। দেবতার ক্ৰোধ; রত্নপ্ৰদীপ : শ্ৰীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (আল্পনা ও জলছবি)
৫। পদ্মফুল; জন্ম-মৃত্যু শৃঙ্খল (আংশিক অনুদিত) : শ্ৰীমণীন্দ্রলাল বসু (মায়াপুরী)
৬। একাকী; প্রেমের প্রথম কলি : শ্ৰীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (হাসি ও অশ্রু)
৭। বউ চোর, রসময়ীর রসিকতা : শ্ৰীপ্ৰভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ষোড়শী, গল্পাঞ্জলি)
৮। গলি; পরীর পরিচয়; নূতন পুতুল; ছবি; সুয়োরানীর সাধ; সমাপ্তি; সমাধান; লক্ষ্যের দিকে; সূর্যস্ত ও সূর্যোদয়; পায়ে চলার পথ; কণ্ঠস্বর; প্রথম শোক; একটি দিবস; শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Schrirabindranath Thakur (লিপিকা)
৯। আঁধারে আলো : শ্ৰীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মেজদিদি)
১০। পাষাণ হৃদয় : শ্ৰীমতী সুনীতি দেবী (বঙ্গবাণী)
এখনই বলে দেওয়া ভাল যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৬ সালে। তার মানে এই নয় যে, এই কজনই তখন নামজাদা লেখক ছিলেন। বরঞ্চ মনে হয়, ভাগনার। ১৯১২২০ এর সময় বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন ও সে যুগে এঁদেরই যে খুব প্রতিপত্তি ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেন বাদ পড়লেন ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্যি মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচনটা ঠিক ভাগনারের হাতে ছিল না। এ দেশ থেকে যে সব বই পাঠানো হয়েছিল, তা থেকে ভাল হোক, মন্দ হোক তাঁকে বাছতে হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের নাম ভাগনার চলতি জর্মন কায়দায় ‘টেগোর’ লেখেন নি।
নানা টীকা-টিল্পনী করা যেত, কিন্তু সেটা পাঠকের কাছে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। জর্মনমন এই গল্পগুলোতেই কেন সাড়া দিল, তার কারণ অনুসন্ধান তাঁরাই করুন।
সাধারণ জর্মনের পক্ষে দুর্বোধ্য কতকগুলো শব্দ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে; যেমন–অগ্নি (দেবতা), অলকা, অন্নপূর্ণ, আরতি, আষাঢ়, B.A. বেলপাতা, ভৈরবী রাগিণী, ভর্তৃহরি, ফুলশয্যা, চোরা বাগান, দোয়েল, জয়দেব যোগাসন, হাতের নোয়া, একতারা, হোলি, হুলুধ্বনি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মেদিনীপুর, শালিগ্রাম, সমুদ্রমন্থন, পয়সা, পানি কৌড়ি, রজনীগন্ধা, রাসলীলা, সাহানা, শুভদৃষ্টি, রথযাত্রা, ব্রাহ্ম সমাজ, ইংরেজি, উড়িয়া বামুন।
সবগুলোর, মানে সব কটাই অতি সংক্ষেপে ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে। মাত্র একটি ভুল—মেঘদূতকে Eops বা মহাকাব্য বলা হয়েছে। উড়ে বামুনরা যে গঙ্গামানের সময় ডলাই-মলাই ও ফোঁটা-তিলক কেটে দেন। সে কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে রান্নার নামে কি বিষ খেতে দেন, সেটা বলতে ভাগনার ভুলে গিয়েছেন। B.A. উপাধি ভাগনার জর্মনদের বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং M.A. যে লাতিন Magister Artium সেটা বলতে ভোলেন নি। আশা করতে পারি আমাদের প্রতি জর্মনদের ভক্তি বেড়েছে।
আম-কাঁঠাল, শিউলি-বকুল বহু গল্পে বার বার এসেছে, কিন্তু ফুল আর ফলের ছয়লাপে ভাগনার ঘাবড়ে গিয়ে সেগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। তবে তিনি রজনীগন্ধার প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদুষ্ট।
অনুবাদ কি রকম হয়েছে? অতি উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পদে পদে ছত্ৰে ছত্রে এই কথাটি বার বার বোঝা যায় যে, দূর বার্লিনে বসে কি গভীর ভালবাসা দিয়ে ভাগনার অনুবাদগুলো করেছেন এবং সেই ভালবাসাই তাকে বাংলার ছোট গল্পের অন্তস্তলে নিয়ে গিয়েছে।
ভৈরবী কোন সময় গাওয়া হয়, ফুলশয্যাতে কে শোয়, মেদিনীপুর কোন দিকে, হাতের নোয়া আর হুলুধ্বনি কাদের একচেট, কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস কে এই সব বিস্তর বায়নাক্কা বরদাস্ত করে জর্মন ১৯২৮ সালে এই বই পড়েছে আর সুদূর বাংলার হৃদিরস আস্বাদন করবার চেষ্টা করেছে।
বর্বর নয় তো কি!
—–
১। রবীন্দ্ৰনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’ থাকতে ভাগনার কেন যে সেগুলো কাজে লাগালেন না, তা বোঝা গেল না!
২। S.D.P.Roy Chowdhury; A. Bhaduri; J.C. Huji; J.Bose; S.C. Bhattacharya.
৩। ইনি শব্দতাত্ত্বিকদের সুপরিচিত।
৪। জীবিত মৃত সকলের নামের পূর্বেই ভাগনার ‘শ্ৰী’ ব্যবহার করেছেন। বাংলা ‘শ’ বুঝতে হলে জর্মানে sch (ইংরাজিতে Schedule-এর sch), ‘জ’ বুঝাতে হলে ‘dsch, চা বুঝাতে হলে ‘sch’, ‘য়’ বুঝাতে হলে ‘J’ ব্যবহার করা হয়েছে।
বিশ্বভারতী
কবি, শিল্পী–স্রষ্টমাত্ৰই স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন। এবং সেই কারণেই আর পাঁচজনের তুলনায় এ জীবনে তারা এমন সব বেদনা পান যার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়ী হতে হলে গণ্ডারের চামড়ার প্রয়োজন—গণ্ডারের চামড়া নিয়ে কোনো কবি আজ পর্যন্ত সার্থক সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি।
জীবনের বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্ৰনাথ বহু অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছিলেন। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ পান; তৎসত্ত্বেও বাঙলাদেশ বহুদিন ধরে তাকে কবি বলে স্বীকার করতে চায় নি। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে বহু গণ্যমান্য লোক এমন সব অন্যায় আক্রমণ এবং আন্দোলন চালান যে রবীন্দ্রনাথকে হয়তো অল্প বয়সে কীটসের মতো ভগ্নহৃদয় নিয়ে ইহলোক পরিত্যাগ করতে হত। রবীন্দ্ৰনাথ যে বহু বেদনা পেয়েও কীটসের মতো ভেঙে পড়েন নি তার অন্যতম প্রধান কারণ, ধর্মে তার অবিচল নিষ্ঠা ছিল এবং দ্বিতীয়টি মহর্ষি স্বহস্তে রবীন্দ্ৰনাথের নৈতিক মেরুদণ্ডটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।
এ জীবনে রবীন্দ্ৰনাথ বহু বেদনা পেয়েছেন এবং তার খবর বাঙালিমাত্রই কিছু না কিছু রাখেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বিশ্বভারতীয় নবপ্রতিষ্ঠান উপলক্ষে, তারই একটি নিবেদন করি।
১৯২১ সালে রবীন্দ্ৰনাথ বিশ্বভারতীর’ প্ৰতিষ্ঠা করেন কিংবা বলতে পারি। যে ইস্কুলটি (পূর্ব বিভাগ) প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে বাঙলা বা বাঙলার বাইরে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল তার সঙ্গে একটি কলেজ (উত্তর বিভাগ) যোগ দিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে প্ৰাচ্য-প্রতীচ্যের নানাপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা করারও ব্যবস্থা হল।
তাই গুরুদেবের বাসনা ছিল, পূর্ব-পশ্চিমের গুণীজ্ঞানীরা যেন শাস্তিনিকেতনে সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সহযোগিতায় বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সাধনায় নিযুক্ত হন।
সেই মর্মে রবীন্দ্ৰনাথ আমন্ত্রণ জানালেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভা লেভিকে। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ববিষয়ে লেভির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল তো বটেই, তদুপরি বৌদ্ধধর্মে বোধ করি তখনকার দিনে পশ্চিমে এমন কেউ ছিলেন না। যিনি তার সামনে সাহস করে দাঁড়াতে পারতেন।
শান্তিনিকেতনে তখন বহুতর পণ্ডিত ছিলেন। শ্ৰীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্ৰীযুত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, শ্ৰীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় এভুজ এবং পিয়ার্সন, শ্ৰীযুত নিতাইবিনোদ গোস্বামী, অধ্যাপক কলিনস বাগদানফ বেনওয়া, ক্রামরিশ, শ্ৰীযুত মিশ্রজী, শ্ৰীযুত হিডজিভাই মরিস, শ্ৰীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও আরো বহু খ্যাতনামা লোক তখন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন।
সঙ্গীতে ছিলেন প্ৰাতঃস্মরণীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের ভিতর ছিলেন শ্ৰীযুত অমিয় চক্রবতী, শ্ৰীযুত প্রমথনাথ বিশী।(১)
এবং আশ্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত না হয়েও এক ঋষি আশ্রমটিকে আপন আশীৰ্বাদ দিয়ে পুণ্যভূমি করে রেখেছিলেন। বাংলাদেশ তাকে প্রায় ভুলে গিয়েছে। ইনি রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরর্বতীকালে লেভি এর পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন।
শান্তিনিকেতন তখন পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের কিছুমাত্র অনটন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর সর্বশেষ কপর্দক দিয়ে-এবং এস্থলে ভক্তিভারে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে এই সব বড় বড় পণ্ডিতেরা যে দক্ষিণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন সে দক্ষিণা আজকের দিনে দিতে গেলে অনেক অপণ্ডিতও অপমান বোধ করবেন।
কিন্তু ছাত্র ছিল না। বিশ্বভারতী তখন পরীক্ষা নিত না, উপাধিও দিত না।
এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, তখনকার দিনে বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রধান নীতি ছিল : ‘দি সিস্টেম অব এগজামিনেশন উইল হ্যাভ নো প্লেস ইন বিশ্বভারতী, নর উইল দ্যার বী। এনি কনফারিং অব ডিগ্ৰীজ।’
এ অবস্থায় বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করতে আসবে কে?
তবে এই যে এত অর্থব্যয় করে বিদেশ থেকে পৃথিবীবরেণ্য পণ্ডিত লেভিকে আনানো হচ্ছে, ইনি বক্তৃতা দেবেন। কার সামনে, ইনি গড়ে তুলবেন কোন ছাত্রকে।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে তখন কোনো যোগসূত্র ছিল না। তবু রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করলেন যাতে করে কলকাতার ছাত্ররা শান্তিনিকেতনে এসে সপ্তাহে অন্তত একটি বক্তৃতা শুনে যেতে পারে। শাস্তিনিকেতনে রবিবার অন্যধ্যায় নয় কাজেই শনিবার বিকেল কিংবা রবির সকালের ট্রেন ধরে যে কোনো ছাত্র কলকাতা থেকে এসে লেভির বক্তৃতা শোনবার সুযোগ পেল।
যেদিন প্রথম বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার কথা সেদিন রবীন্দ্রনাথ খবর নিয়ে জানতে পারলেন। কলকাতা থেকে এসেছেন মাত্র দুটি ছাত্র: তারও একজন রসায়নের ছাত্র আর পাঁচজন যে রকম ‘বোলপুর দেখতে’ আসে এই সুযোগে সেও সেই রকম এসেছে!
বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তখন বারো জনও হবে না। তার মধ্যে সংস্কৃত পড়তেন জোর চারজন।
এই ছটি ছাত্রের সামনে (অবশ্য পণ্ডিতরাও উপস্থিত থাকবেন)। বক্তৃতা দেবেন। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত লেভি! রবীন্দ্রনাথ বড় মর্মাহত হয়েছিলেন।
তাই প্রথম বক্তৃতায় ক্লাসের পুরোভাগে খাতকলম নিয়ে বসলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। লেভির আর কোনো খেদ না থাকারই কথা।
——-
(১) সিংহলের শ্রমণ পণ্ডিতদ্বয় এবং আরও কয়েকজনের নাম ভুলে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে লজিজত আমি।
বেমক্কা
বন্ধুবর
গুলাম কুদ্দুসকে–
লোকসঙ্গীত ও বিদগ্ধ সঙ্গীতে যে পার্থক্য সেটা সহজেই আমাদের কানো ধরা পড়ে, তেমনি লোকসাহিত্য ও বিদগ্ধ সাহিত্যের পার্থক্য সম্বন্ধেও আমরা বিলক্ষণ সচেতন। আর্টের যে-কোনো বিভাগেই-নাট্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য-ত সে যাই হোক না কেন, এই বিদগ্ধ এবং লোকায়ত রসসৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যটা আমরা বহুকাল ধরে করে আসছি।
তাই বলে লোকসঙ্গীত কিম্বা গণ-সাহিত্য নিন্দনীয় এ-কথা কোনো আলঙ্কারিকই কখনো বলেন নি। বাউল ভাটিয়াল বর্বরতার লক্ষণ কিম্বা বারমাসী যাত্রাগান রসসৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না, এ-কথা বললে আপন রসবোধের অভাব ঢাক পিটিয়ে বলা হয় মাত্র।
কিন্তু যখন এই লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্য শহরের মাঝখানে স্টেজের উপর সাজিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাড়ম্বরে শোনানো এবং দেখানো হয় তখনই আমাদের আপত্তি। যখনই বলা হয় এই সাঁওতাল নাচের সামনে ভরতনৃত্যম হার মানে কিম্বা বলা হয় এই ‘রাবণবধ’ পালা ‘ডাকঘরে’র উপর ছক্কা-পাঞ্জা মেরেছে–তোমরা অতিশয় বেরসিক বর্বর বুৰ্জ্জুয়া বলে এ তত্ত্বটা বুঝতে পারছে না, তখন নিরীহ বুজুয়া হওয়া সত্ত্বেও আপত্তি না করে থাকতে পারি নে।
কথাটা খুলে বলি। লোকসঙ্গীত (এবং বিশেষত গণ-নৃত্য) ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পার্থক্য অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু একটা পার্থক্য এস্থলে বলে নিলে আমার প্রতিবাদের মূল তত্ত্বটা পাঠক সহজেই ধরে নিতে পারবেন। এই ধরুন, সাঁওতাল কিংবা গুজরাতের গরবা নাচ। এগুলো গণ-নৃত্য এবং এর সবচেয়ে বড় জিনিস এই যে, এ নাচে সমাজ বা শ্রেণীর সকলেই হিস্যাদার। চাঁদের আলোতে, না-ঠাণ্ডা না-গরম আবহাওয়াতে জনপদবাসী যখন দুদণ্ড ফুর্তিফার্তি করতে চায়, তখন তারা সকলেই নাচতে শুরু করে। যাদের হাড় বড় বেশি বুড়িয়ে গিয়েছে তারা ঘরে শুয়ে থাকে, কিন্তু যারা আসে তাদের কেউই নাচ থেকে বাদ যায় না। হয় নাচে, না হলে ঢোল বাজায়—বাচ্চা কোলে নিয়ে আধ্যবয়সী মাদেরও নাচের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। তাই বলা যোতে পারে সাঁওতাল কিম্বা গরবা নাচ-অর্থাৎ তাবৎ গণ-নৃত্যুই-নাচা হয় আপন আনন্দের জন্য, লোককে দেখানোর জন্য কিম্বা ‘লোক দেখানোর জন্য নয়। অর্থাৎ লোকনৃত্যে দর্শক থাকে না।
কিন্তু যখন উদয়শঙ্কর নাচেন তখন আমরা সবাই ধেই ধেই করে নেচে উঠি নে, কিম্বা যখন খানসায়েব চোখ বন্ধ করে জয়জয়ন্তী ধরেন তখন আমরা আর সবাই চেল্লাচেল্লি করে উঠি নে। ইচ্ছে যে একদম হয় না সে-কথা বলতে পারি নে, তবু যে করি নে। তার একমাত্র কারণ উদয়শঙ্করের সঙ্গে পা মিলিয়ে কিম্বা খানসাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রসসৃষ্টি আমরা এক মুহূর্তের তরেও করতে পারি নে। (যদি পারতুম। তবে উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য, খানসাহেবের গান শোনবার জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করতুম না-কিম্বা বলতে পারেন, সিংগীর গলায় আপন মাথা ঢোকাতে পারলে সার্কাসে যেতুম না)।
তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কিম্বা নৃত্যের জন্য শ্রোতা এবং দর্শকের প্রয়োজন।
লোকনৃত্যে যখন সবাই হিস্যা নিতে পারে আপনি পা চালিয়েই, তখন এ কথা আশা করি সকলেই মেনে নেবেন যে, সে নৃত্য খুব সরল হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে সূক্ষ্ম পায়ের কাজ থাকার কথা নয়, ভাবভঙ্গী প্রকাশের জন্য দুর্বোধ্য মুদ্রা সেখানে থাকতেই পারে না। এবং তাই বলা যেতে পারে, সে নৃত্যে আর যা থাকে থাকুক, বৈচিত্র্য থাকতে পারে না।
তাই গণ-নৃত্য মাত্রই একঘেয়ে।
কমুনিস্ট ভায়ারা (কমরেডরা) মনস্থির করেছেন গণ-কলা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কলা এবং সেই গণ-নৃত্য শহরে বুৰ্জ্জুয়াদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। তাই মেহন্নত, ততোধিক তাকলিফা বরদাস্ত করে তারা শহরে স্টেজ খাটান, পর্দা ঝোলান, রঙ-বেরঙের আলোর ব্যবস্থা করেন। আর তারপর চালান হৈদ্রাবাদী কিম্বা কুয়াম্বতুরেরও হতে পারে,— জানি নে, ধোপার নাচ। কিম্বা গুজরাতী গরীবা! বলেন, ‘পশ্য, পশ্য’—থুড়ি, দ্যাখ, দ্যাখ, এরেই কয় লাচ।’
পূর্বেই নিবেদন করেছি। গণ-নৃত্য নিন্দনীয় নয়, কিন্তু যে গণ-নৃত্য একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন হতে বাধ্য, সেই নাচ দেখতে হবে ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে? ঘন ঘন হাততালি দিয়ে বলতে হবে ‘মরি, মরি’? দু-চার মিনিটের তরে যে এ নাচ দেখা যায় না, সে কথা বলছি নে।
আলো-অন্ধকারে ভিন গাঁয়ে যাচ্ছেন, দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন, চাঁদ উঠি উঠি করেও উঠছেন না–এমন সময় দেখতে পেলেন গায়ের মন্দিরের আঙিনায় একপাল মেয়ে মাথায় ছ্যাদা-ওলা কলসীতে পিদিম রেখে চক্কর বানিয়ে ধীরে ধীরে মন্দমধুর পা ফেলে নাচছে। জানটা তার হয়ে গেল। দুমিনিট দাঁড়িয়ে আলোর নাচ আর মেয়েদের গান, ‘সোনার দেওর, আমার হাত রাঙাবার জন্য মেহেদী এনেছ কি?’ দেখে নিলেন। কিন্তু তারপর? যে নাচ আস্তে আস্তে বিকাশের দিকে এগিয়ে যায় না, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গ, পদবিন্যাসের ভিতর দিয়ে যে নাচ পরিসমাপ্তিতে পৌঁছয় না, সে নাচ দেখবেন কতক্ষণ ধরে? এ-নাচের পরিসমাপ্তি কোনো রসসৃষ্টির আভ্যন্তরীণ কারণে হয় না, এর পরিসমাপ্তি হয় নর্তকীরা যখন ক্লাস্ত হয়ে পড়েন তখনই।
আলো-অন্ধকার, চাদ উঠি-উঠি, শ্যাওলামাখা ভাঙা দেউলের পরিবেশ থেকে হাঁচিকা টানে ছিড়ে-নিয়ে-আসা নৃত্য শহরের স্টেজে মূৰ্ছা তো যায় বটেই, তার উপর মাইক্রোফোনযোগে চিৎকার করে তারস্বরে আপনাকে বলা হয়, ‘এ নাচ বড় উমদা নাচ-’। এ নাচ আপনাকে দেখতে হয় আধঘণ্টা ধরে! আধঘণ্টা ধরে দেখতে হয় সেই নাচ, যার সর্ব পদবিন্যাস মুখস্থ হয়ে যায় আড়াই মিনিটেই।
পনরো টাকার সীটে বসে (টাকাটা দিয়েছিলেন আমার এক গোলাপী অর্থাৎ নিমকমুনিস্টি কমরেড) আমি আর থাকতে না পেরে মুখে আঙুল পুরে শিটি দিয়েছিলুম প্ৰাণপণ। হৈ হৈ রৈ রৈ। মার মার কাট কাট। এ কী বর্বরতা?
আমি বললুম, ‘কেন বাওয়া, আপত্তি জানাবার এই তো প্রলেটারিয়েটস অব দি প্রলেটারিয়েট কায়দা।’
বড় দিন
বাইবেলে বলা হয়েছে পূব থেকে তিন জন ঋষি প্যালেস্টাইনের জুডেয়া প্রদেশের রাজা হেরোডের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইহুদিদের নবীন রাজা কোথায় জন্ম নিয়েছেন? আমরা পূর্বকাশে তাঁর তারা দেখতে পেয়ে তাকে পুজো করতে এসেছি।
সেই তারাই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বোৎলেহেম-যেখানে প্ৰভু যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। মা মেরী আর তার বাগদত্ত যোসেফ পান্থশালায় স্থান পান নি বলে আশ্রয় নিয়েছিলেন পান্থশালার অশ্বালয়ে। তারই মাঝখানে কুমারী মেরী জন্ম দিলেন এ জগতের নব জন্মদাতা প্ৰভু যীশুকে।
দেবদূতরা মাঠে গিয়ে রাখাল ছেলেদের সুসংবাদ দিলেন-প্ৰভু যীশু, ইহুদিদের রাজা জন্ম নিয়েছেন। তারাও এসে দেখে, গাধা-খচ্চর, খড়-বিচুলির মাঝখানে মা-জননীর কোলে শুয়ে আছেন রাজাধিরাজ।
এই ছবিটি এঁকেছেন যুগ যুগ ধরে বহু শিল্পী, বহু কবি, বহু চিত্রকর। নিরাশ্রয়ের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন বিশ্বজনের আশ্রয়-দাতা।
* * *
বাইরের থেকে গভীর গুঞ্জরণ শুনে মনে হল বিদ্যালয়ের ভিতর বুঝি তরুণ সাধকেরা বিদ্যাভ্যাস করছেন। জানা ছিল টোল-মাদ্রাসা নয়, তাই ভিতরে ঢুকে ভিরমি যাই নি।
ক’শ নারী পুরুষ ছিলেন আদম-শুমারী করে দেখি নি। পুরুষদের সবাই পরে এসেছেন ইভূনিং ড্রেস। কালো বনাতের চোস্ত পাতলুন-তাঁর দুদিকে সিল্কের চকচকে দু ফালি পট্টি; কচ্ছপের খোলের মত শক্ত শার্ট, কোণভাঙা কলার-ধবধবে সাদা; বনাতের ওয়েসটু কোট আর কোটের লেপেলে সেই সিল্কের চকচকে ট্যারচা পট্টি; কালো বো। ফুটে উঠেছে সাদা শার্ট কলারের উপর-যেন শ্বেত সরোবরে কৃষ্ণা কমলিনী। পায়ে কালো বার্নিশের জুতো—হাতে গেলাস।
কিংবা শার্ক-স্কিনের ধরনের সাদা মসৃণ পাতলুন। গায়ে গলাবন্ধ প্রিনস কোট’- সিক্স-সিলিন্ডারি অর্থাৎ ছ-বোতামওয়ালা। কারো বোতাম হাইদ্রাবাদী চৌকো, কারো বা বিন্দরী গোল-কালোর উপরে সাদা কাজ। একজনের বোতামগুলো দেখলুম খাস জাহাঙ্গীরশাহী মোহরের l-হাতে গেলাস।
তারি মধ্যিখানে বসে আছেন এক খাঁটি বাঙালি নটবর। সে কী মোলায়েম মিহি চুনটকরা শান্তিপুরে ঘি রঙের মেরিনার পাঞ্জাবি আর তার উপরে আড়করা কালো কাশ্মীরী শালে সোনালি জরির কাজ। হীরের আংটি বোতাম ম্যাচ করা, আর মাথায় যা চুল তাকে চুল না। বলে কৃষ্ণমুকুট বললেই সে তাজমহলের কদর দেখানো হয়। পায়ে পাম্পসু-হাতে গেলাস।
‘দেশসেবক ও দু’একজন ছিলেন। গায়ে খন্দর-হাতে? না, হাতে কিচ্ছ না। আমি আবার সব সময় ভালো করে দেখতে পাই নে-বয়স হয়েছে।
কিন্তু এ সব নস্যি। দেখতে হয় মেয়েদের। ব্যাটাছেলেরা যখন মনস্থির করে ফেলেছে, সাঁঝের ঝোকে সাদা কালো ভিন্ন অন্য রঙ নিয়ে খেলা দেখাবে না। তখন এই দুই স্বর সা আর রে দিয়ে কি ভেস্কিই বা খেলবে?
হোথায় দেখো, আহা-হা-হা! দুধের উপর গোলাপী দিয়ে ময়ুরকষ্ঠী-বাঙ্গালোরী শাড়ি! জরির আঁচল! আর সেই জরির আঁচল দিয়ে ব্রাউজের হাতা। ব্লাউজের বাদ-বাকি দেখা যাচ্ছে না, আছে কি নেই। তাই বলতে পারব না। বোধ হয় নেই—না থাকাতেই সৌন্দর্য বেশি। ফরাসীরা কি এ জিনিসকেই বলে ‘দোকোলতে’? বুক-পিঠ-কাটা মেমসায়েবদের ইভনিং ফ্রক এর কাছে লজ্জায় জড়সড়।
ডান হাতে কনুই অবধি সোনার চুড়ি-বঁ হাতে কবজের মত বাঁধা হোমিওপ্যাথিক রিস্টওয়াচ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ডিনারের কত বাকি? কটা বেজেছে?’ বলেই লজ্জা পেলেন, কারণ ভুলে গিয়েছিলেন নিজের হাতেই বাঁধা রয়েছে ঘড়ি। কিন্তু লাল হলেন না, কারণ রুজ আগে-ভাগেই এত লাল করে রেখেছে যে, আর লাল হবার ‘পার্কিঙপ্লেস’ নেই।
হাতে? যান মশাই,-আমার অতশত মনে নেই। হালকা সবুজ জর্জেটের সঙ্গে রক্তেরাঙা ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বঁ হাতে ঝুলছে ব্যাগ, কিন্তু ব্যাগের স্ট্র্যাপটার রঙ মেলানো রয়েছে রক্ত-রাঙা ব্লাউজের সঙ্গে এবং তাকে ফের মেলানো হয়েছে স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে। আর কোথায় কোথায় মিল অমিল আছে দেখবার পূর্বেই তিনি সরে পড়লেন। ডান হাতে কিছু ছিল? কী মুশকিল!
আরে! মারোয়াড়ি ভদ্রলোকরা কি পাটিতে মহিলাদের আনতে শুরু করেছেন? কবে থেকে জানতুম না তো।
একদম খাঁটি মারোয়াড়ি শাড়ি। টকটকে লাল রঙ-ছোটো ছোটো বোট্টাদার। বেনারসী র্যাপার। সেই কাপড় দিয়েই ব্লাউজ-জরির বোট্টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সকাল বেলা হাওড়ায় নামলে ব্রিজ পেরিয়ে হামেশাই এ রকম শাড়ি দেখতে পাই–মহিলারা স্নান সেরে ফিরছেন। সেই শাড়ি এখানে? হাতে আবার লাইফ বেল্ট সাইজের কাঁকন।
মাথার দিকে চেয়ে দেখি, না, ইনি মারোয়াড়ি নন। চুলটি গুটিয়েছেন একদম পাকাপোক্ত গ্রেতা গার্বে স্টাইলে। কঁধের উপর নেতিয়ে পড়ে ডগার দিকে একটুখানি ঢেউখেলানো। শুধুচুলটি দেখলে তামা-তুলসী স্পর্শ করে বলতুম, জীবনের শেষ স্বপ্ন সফল হল-গ্রেতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে। কিন্তু কেন হেন জঙ্গলি শাড়ির সঙ্গে মডার্ন চুল?
নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে ধ্যান করে হৃদয়ঙ্গম করলুম তত্ত্বটা। শাড়ি ব্লাউজের কনট্রাসট ম্যাচিঙের দিন গেছে। এখন নব নব কনট্রাসট-এর সন্ধান চলেছে। এ হচ্ছে প্রাচীন পন্থা আর আধুনিক ফ্যাশানের দ্বন্দ্ব। গলার নীচে ত্রয়োদশ শতাব্দী-উপরে বিংশ। প্রাণভরে বাঙালি মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করলুম। উচ্চকণ্ঠে করলেও কোনো আপত্তি ছিল না। সে হট্টগোলের ভিতর এটম বামের আওয়াজও শোনা যেত না। কি করে খানার ঘণ্টা শুনতে পেলুম, খোদায় মালুম।
হাওড়া থেকে শেয়ালদা সাইজের খানা-টেবিল। টার্কি পাখিরা রোস্ট হয়ে উধৰ্বপদী হয়েছেন অন্তত শাজনা, মুরগী-মুসল্লম অগুনতি, সাদা কেঁচোর মত কিলবিল করছে ইতালির মাক্কারোনি হাইনৎসের লাল টমাটো সসের ভিতর, আন্ডার রাশান স্যালাড গায়ে কম্বল জড়িয়েছে প্যোর ব্রিটিশ মায়েনেজের ভিতর, চকলেট রঙের শিককাবাবের উপর আঁকা হয়েছে সাদা পেঁয়াজ-মূলোর আলপনা, গরম মশলার কাথের কাদায় মুখ গুঁজে আছেন রুইমাছের ঝাঁক, ডাঁটার মত আটা আটা এসপেরেগাস টিন থেকে বেরিয়ে শ্যাম্পেনের গন্ধ পেয়ে ফুলে উঠেছে, পোলাওয়ের পিরামিডের উপর সসেজের ডজন ডজন কুতুবমিনার।
প্ৰভু যীশু জন্ম নিলেন খড়বিচুলির মাঝখানে—আর তার পরব হল শ্যাম্পেনে টার্কিতে!!
রবীন্দ্ৰনাথ বলেছেন,-
‘নামিনু শ্ৰীধামে। দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্ৰাণটা করিল কণ্ঠাগত!’
এর পর পাণ্ডাদের সহ্যদয় অত্যাচারের কথা ফলিয়ে বলবার মত সাহস আমাদের মত অর্বাচীন জনের হওয়ার কথা নয়। ওস্তাদরা যখন মিয়াকী তোড়ী’ অর্থাৎ মেয়া তানসেন রচিত তোড়ী রাগিণী গান তখন গাওয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দুহাত দিয়ে দুটি কান ছুয়ে নেন। ভাবখানা এই ‘হে গুরুদেব, ওস্তাদের ওস্তাদ, যে-গান তুমি গেয়েছ সেটি গাইবার দম্ভ যে আমি প্রকাশ করলুম, তার জন্য আগে-ভাগেই মাপ চাইছি।’ সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদেরও তাই করা উচিত-মাইকেলও তাই করেছেন। আদি কবির স্মরণে বলেছেন, ‘রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে।’ কালিদাসও বলেছেন,-সংস্কৃতটা মনে নেই—’বজ্রমণি ছেদ করার পর সূত্র যেমন অনায়াসে মণির ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে, বাল্মীকির রামায়ণের পর আমার রঘুবংশ ঠিক সেইরূপ।’
শুধু এইটুকু বলে রাখি, পাণ্ডা বলতে ভারতীয় যে মহান জাতের কথা ওঠে তার কোনো জাত নেই। অর্থাৎ শ্ৰীধামের পাণ্ডা। আর আজমীঢ়ের মুসলমান পাণ্ডাতে কোনো পার্থক্য নেই-যাত্রীর প্রাণটা নিমেষে কণ্ঠাগত করবার জন্য এঁদের বজমুষ্টি ভারতের সর্বত্রই এক প্রকার। ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলনের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে? কংগ্রেস যদি এঁদের হাতে দেশের ভারটা ছেড়ে দিতেন তবে ভারত ছেদের যে কোনো প্রয়োজন হ’ত না সে বিষয় আমি স্থির-নিশ্চয়। এর জন্য মাত্র একটি প্রমাণ পেশ করছি। উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সর্বপ্রকারের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ সে কথা সবাই জানেন; কিন্তু এ তথ্যটি কি লক্ষ্য করেছেন যে, শিখরা তীৰ্থ করবার জন্য দিব্য পাকিস্তান যাচ্ছেন, পাকিস্তানের মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের আজমীঢ় আসছেন, পূর্ব-পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রাম যাচ্ছেন? পাণ্ডার ব্যবসা দুনিয়ার প্রাচীনতম ব্যবসা—ওটাকে নষ্ট করা কংগ্রেস লীগের কর্ম নয়।
সে কথা যাক। আমি বলছিলুম, বিদেশ যাওয়ার পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল পাণ্ডাজগতের অশোক-স্তম্ভ এবং কুতুবমিনার ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান পাণ্ডা। জেরুজালেমে গিয়ে সে ভুল ভাঙিল।
আমি তীর্থপ্ৰাণ। অর্থাৎ তীর্থ দেখলেই ফুল চড়াই, শীরণী’ বিলাই। ভারতীয় তাবৎ তীর্থ যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন গেলুম জেরুজালেম। ইহুদি, খ্ৰীষ্টান, মুসলমান এই তিন ধর্মের ত্ৰিবেণী জেরুজালেমে। বিশ্বপাণ্ডার ইউ.এন. ও. ঐখানেই। সেখান থেকে গেলুম বোৎলেহেম-প্ৰভু যীশুর জন্মস্থান।
বড়দিনের কয়েক দিন পরে গিয়েছিলুম। জেরুজালেম-বোৎলেহেমের বাস সার্ভিস আমাদের স্টেট বাসের চেয়ে অনেক ভালো (বাসের উপর পলায়মান ব্যান্ত্রের ছবি এঁকে কর্তারা ভালই করেছেন—বাঘ পর্যন্ত ভিড় দেখে ভয়ে পালাচ্ছে)। পকেটে গাইড বুক-পাণ্ডার ‘এরজাৎস’-কঁধে ক্যামেরা—হাতে লাঠি। আধা ঘণ্টার ভিতর বোৎলেহেম গ্রামে নামলুম।
ভেবেছিলুম, দেখতে পাবো, বাইবেল-বর্ণিত ভাঙাচোরা সরাই আর জরাজীর্ণ আস্তাবল-যেখানে র্যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। সব কঙ্গুর। সব কিছু ভেঙেচুরে তার উপর দাঁড়িয়ে এক বিরাট গির্জা।
গির্জাটি প্ৰিয়দৰ্শন অস্বীকার করি নে। আর ভিতরে মেঝের উপর যে মোজায়িক বা পাথরে-খচা। আলপনা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত রসদৃষ্টি সেন্ট সোফিয়া, সেন্ট পল কোথাও আমি দেখি নি। সে কথা আরেক দিন হবে।
গাইড বুকে লেখা ছিল, গির্জার নিচে ভূগর্ভে এখনো আছে সেই আস্তাবল-যেখানে প্ৰভু যীশু জন্মগ্রহণ করেন। সেই গহ্বরে ঢুকতে যেতেই দেখি সামনে এক ছ-ফুটি পাণ্ডা। বাবরী চুল, মান-মনোহর গালি-কম্বল দাঁড়ি, ইয়া গোপ, মিশকালো আলখাল্লা, মাথায় চিমনির চোঙার মত টুপি, হাতে মালা-তার এক একটি দানা বেবি সাইজের ফুটবলের মত। পাষ্ট্ৰীপাণ্ডার অর্ধ-নারীশ্বর।
গুরু-গভীর কণ্ঠে শুধাল, ‘হোয়াট ল্যানগুইজ? কেল লীগ? বেলশে শপ্ৰাখে? লিসান এ?’—প্রায় বারোটা ভাষায় জিজ্ঞেস করল আমি কোন ভাষা বুঝি।
সবিনয় বললুম, ‘হিন্দুস্থানী।’
বলবে, ‘দস পিয়াস্তর।’ অর্থাৎ দশ পিয়াস্তুর (প্রায় এক টাকা) দৰ্শনী দাও।
‘দস’ ছাড়া অন্য কোন হিন্দুস্থানী সে জানে না বুঝলুম, কিন্তু তাই বা কি কম? আমি অবাক হয়ে ইংরেজিতে বললুম, ‘প্ৰভু যীশুর জন্মভূমি দেখতে হলে পয়সা দিতে হয়?’
বললে, ‘হ্যাঁ।’
অনেক তর্কাতর্কি হল। আমি বুঝিয়ে বললুম, ‘আমি ভারতীয়, খ্ৰীষ্টান নই, তবু সাতসমুদ্র-তেরো-নদী পেরিয়ে এসেছি সেই মহাপুরুষের জন্মভূমি দেখতে যিনি সবচেয়ে বেশি। চেষ্টা করেছিলেন গরিব-ধনীর তফাত-ফারাক ঘুচিয়ে দেবার জন্য, যিনি বলেছিলেন কেউ কামিজটা চাইলে তাকে জোব্বাটি দিয়ে দেবে-আর তার জন্মভূমি দেখবার জন্য দিতে হবে পয়সা?
শুধু যে চোরাই ধর্মের কাহিনী শোনে না তা নয়। আমি উলটো পথ নিলুম-পাণ্ডা ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।
গাইড বুকে লেখা ছিল, গহ্বরে যাবার দুটি রাস্তা। একটি গ্ৰীক অর্থডক্স প্রতিষ্ঠানের জিন্মায়, অন্যটি রোমান ক্যাথলিকদের। গেলুম সেটির দিকে-গির্জাটি ঘুরে সেদিকে পৌঁছতে হয়।
এখানে দেখি আরেক পাণ্ডা-যেন পয়লাটার যমজ। বেশভূষায় ঈষৎ পার্থক্য।
পুনরপি সেই সদালাপ’। ‘ফেলো কড়ি মাখো তেল।’ অম্মো না-ছোড়-বন্দা।
দিল-দরাজ, খোলা-হাত পাঠক হয়ত অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন, ‘তুমি তো আচ্ছা ত্যাঁদোড় বাপুঃ এত পয়সা খর্চা করে পৌঁছলে মোকামে—এখন দু-পয়সার চাবুক কিনতেচাও না হাজার টাকার ঘোড়া কেনার পর?’ তা নয়, আমি দেখতে চাইছিলুম পাণ্ডাদের দৌড়টা কতদূর অবধি।
এবারে হার মানবার পূর্বে শেষ বাণ হানলুম।
বললুম, ‘দেশে গিয়ে কাগজে লিখব, রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান কি রকম প্ৰভু যীশুর জন্মস্থান ভাঙিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। আমাদের দেশেও কমুনিটি আছে।’
বলে লাঠিটা বার তিনেক পাথরে ঠুকে ফিরে চললুম ঘোঁত-ঘোঁত করে বাস স্ট্যান্ডের দিকে।
পাণ্ডা ডাকলে, ‘শোন।’
আমি বললুম, ‘হুঁঃ!’
‘তুমি সত্যি এত টাকা খরচ করে এখানে এসে দশ পিয়াস্তরের জন্য তীর্থ না দেখে চলে যাবে?’
‘আলবত। প্রভুর জন্মভূমি দেখার জন্য পয়সা দিয়ে প্রভুর স্মৃতির অবমাননা করতে চাই নে।’
খ্যাঁস-খ্যাঁস করে দাড়ি চুলকোল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ফিস-ফিস করে কানের কাছে মুখ-বোটকা রসুনের গন্ধ—এনে বলল, ‘যদি প্রতিজ্ঞা করো কাউকে বলবে না ফ্রী ঢুকতে দিয়েছি, তবে-’
আমি বললুম, আচ্ছা, এখানে তোমার ব্যবসা মাটি করব না। কিন্তু দেশে গিয়ে বলতে পারব তো?’
তখন হার মানল। আমরা বহু লঙ্কা জয় করেছি!!
ভারতীয় নৃত্য
নৃত্য জীবনীশক্তির চরম বিকাশ। যে-সব কলা দ্বারা মানুষ তাহার সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশ করে, তাহাদের গভীরতম মূল নৃত্যরস হইতে প্রাণসঞ্চয় করে। অন্যান্য কলা সৃষ্টি হইবার বহু পূর্বে মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত, আড়ম্বরহীন নৃত্য দ্বারা তাহার অনুভূতি প্ৰকাশ করিয়াছে—অপরের হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারিত করিবার জন্য এই সরল কলাই তখন তাহার একমাত্র আশ্রয়ও ছিল। আদিম মানবের বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে সে তখনও শিখে নাই, প্রতিমা নির্মাণের যন্ত্রপাতি তাহার ছিল না, চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম তাহার কাছে তখনও অজানা। অনুভূতি প্রকাশ করিবার একমাত্র পন্থা ছিল তাহার নিজের দেহ; সেই দেহ সে সাবলীল ছন্দে তালে তালে আন্দোলিত করিয়া তাহার সুখ-দুঃখ, ভয়-ঘৃণা প্রকাশ করিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপ গ্ৰহণ করিতে লাগিল-নৃত্যও তাহার সঙ্গে যোগ রাখিয়া সুকুমার কলায় পরিণত হইল; মানুষ নৃত্য দ্বারা তাহার সূক্ষ্মতম ও গভীরতম অনুভূতিকে রূপ দিতে শিখিল।
সলিল ছন্দে, তালমানযোগে দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আন্দোলন দ্বারা মানুষ যখন তাহার জীবনীশক্তির চরম সত্তাকে সপ্রকাশ করিয়া তুলে তখনই তাঁহা নৃত্যের রূপ ধারণ করে। নৃত্য তখন মানুষের নব নব সৌন্দর্যানুভূতি, সত্যের সঙ্গে তাহার অন্তরতম পরিচয় নব নব রূপে উন্মোচন করিয়া প্রকাশ করে। তাই শুদ্ধ, অকৃত্ৰিম নৃত্য সম্পূর্ণ বাধাবন্ধহীন। দেশ ও কালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে তাহাকে রুদ্ধ করা, কুসংস্কার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করার অর্থ আর কিছুই নয়—তাহার অফুরন্ত জীবন-উৎসকে রুদ্ধ করা, তাহার স্বাধীনতাকে পঙ্গু করা। আমাদের দেশের হৃদয় একদিন স্বতঃস্ফুর্ত, বাধাবন্ধহীন আনন্দের নৃত্যছন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল, আজ সেই ধারা বইন্ধ হইয়া ব্যবসায়ী নটনটীদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকূপের সৃষ্টি করিয়াছে। রোগজীৰ্ণ, বিষাক্ত, বিলাসব্যসনীদের উত্তেজনা দানেই আজ তাহার চরম আনন্দ, পরম লাভ। ক্ষুদ্র হৃদয়ের অবসর বিনোদন ও ক্ষণস্থায়ী চিত্তচাঞ্চল্যের প্রকাশ করাকেই এখন নৃত্যের আদর্শ বলিয়া ধরিয়ালওয়া হইয়াছে।
কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের সুস্থবুদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে; নৃত্যের বিকৃত বিকলাঙ্গ দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্জীবিত হইতেছে। ভারতীয় নৃত্যের নবজীবন সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভারতের উচ্চাঙ্গ ও জনপদ নৃত্যের বিভিন্ন ধারার সহিত পরিচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।
সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অনুন্নত জাতির ভিতরে যে-সব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে ফসল কাটা, নবান্নের আনন্দ অথবা বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, ভূতপ্রেতের লীলাখেলা। বসুন্ধরার আদিম সন্তান নৃত্যযোগে প্রয়োজন মত কখনো প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছে, কখনো তাহার দক্ষিণ মুখের কামনা করিয়াছে। ডমরু ঢোলের বৈচিত্র্যহীন তালের সঙ্গে সে তখন তাহার দেহের ছন্দ মিলাইয়া নাচিয়াছে। সে নৃত্য মার্জিত, কিন্তু তবু কখনও কখনও তাঁহাতে হিল্লোলের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্ধবৃত্তাকারে তাহারা নাচে, গান গায় ও মধ্যস্থলে দুইজন পুরুষ মাদল বাজাইয়া তীক্ষ্ণ চিৎকার ও উন্মত্ত নৃত্যে স্ত্রীলোকদিগকে দ্রুততর নৃত্যে উত্তেজিত করে। পুরুষেরাও কখনো মূল নতর্করাপে অপ্ৰসন্ন দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য অথবা দর্শকের মনে বিচিত্ৰ ভাব সঞ্চারের জন্য নৃত্য করিয়া থাকে। অসভ্য সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তিও অসীম; সমাজ তাহাদিগকে ভক্তিভরে পূজা করে।
আমাদের দেশের জনপদ নৃত্য বলিতে প্রধানত গুজরাতের গরবা, মালাবারের কৈকট্টকলি, উত্তর-ভারতের কাজরী ও মণিপুরের রাসলীলাই বুঝায়। ইহাদের মূলে ধর্মের অনুপ্রেরণা, অঙ্গভঙ্গিতে ইহারা সুমার্জিত ও আঙ্গিকের দিক দিয়া যে ইহাদের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নৃত্যগুলি পুনরাবৃত্তিবহুল বলিয়া দর্শকের মন সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসত্ত্বেও ইহাদের মাধুর্য ও প্রাণশক্তি অস্বীকার করা যায় না। গুজরাতের গরবাতে যথেষ্ট লালিত্য ও প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু পদভঙ্গির অভাব; মালাবারের কৈকট্রকলিতে সবল অঙ্গ সঞ্চালন ও বিচিত্র পদভঙ্গির প্রাচুর্য আছে, কিন্তু মাধুর্যের অভাব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, একমাত্র গুজরাতের জনপদ নৃত্যেই স্ত্রী-পুরুষেরা যেমন পৃথক পৃথক মণ্ডলীতে নৃত্য করিয়া থাকে, সেইরূপ উভয়ে সম্মিলিত হইয়াও নৃত্য করিবার রীতি প্রচলিত আছে। নর্তকীরা বহু ছিদ্রবিশিষ্ট মৃৎপাত্রে জ্বলন্ত প্ৰদীপ রাখিয়া অথবা মস্তকে সুগঠিত পিত্তল কলসী ধারণ করিয়া মনোরম অঙ্গভঙ্গিতে চক্রাকারে নৃত্য করে; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও রাসগীতি গায়, করতালি দিয়া তাল লয় রক্ষা করে। কখনও কখনও দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নাচিবার সময় তাল বাজায়; অজন্তা ও অন্যান্য প্রাচীন চিত্রে ঐ কাষ্ঠখণ্ডের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সঙ্গীত সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; তখন কেবলমাত্র মাদলের তালে শুদ্ধ স্বাধীন নৃত্য আরম্ভ হয়; অঙ্গভঙ্গি তখন সবল হইয়া ওঠে ও পদসঞ্চালন দ্রুততর গতিতে হইতে থাকে।
জনপদনৃত্যের মধ্যে মণিপুরী রাসলীলাতেই সর্বাধিক সাধনা ও শিক্ষার প্রয়োজন হয়; আঙ্গিকের দিক দিয়াও উন্নত বলিয়া রাসলীলাকে উচ্চাঙ্গ নৃত্যরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মণিপুরের রাসলীলা ভক্তিরসে পরিপূর্ণ—গোপ ও গোপীগণের আবেষ্টনীতে শ্ৰীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বর্ণনা করাই এই নৃত্যের উদ্দেশ্য। রাজবাড়িতে রাসলীলার নাচ শিখানো হয়, ও দেশের জনসাধারণের রসের দিক দিয়া ইহার বিচার করিয়া ইহার প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রাসলীলায় তরুণীরা ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীতে গোপীরূপে নৃত্য করে ও রাধার ভূমিকায় বালককে নামানো হয়। তরুণীদের নৃত্য অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সরল; তরুণ ও বয়স্কদের নৃত্য সবল ও ছন্দ-বৈচিত্র্যবহুল। নাচের তাল রক্ষা হয় মৃদঙ্গর জ্ঞাতি, খোল সংযোগে।
উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে প্রধান—উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ-ভারতের ভরত নাট্যম ও মালাবারের কথাকলি ও মোহিনী আট্যম। পরিতাপের বিষয় এই সব কয়টি নৃত্যই ব্যবসাদার নটনটীর কবলগ্ৰস্ত হইয়া উচ্ছঙ্খল বিত্তশীলাদের ঘূণ্য লালসাগ্নি উদ্দীপ্ত ও চরিতার্থকরিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। যে দুষ্ট পরিবেষ্টনীর মধ্যে এইসব নৃত্যের চর্চা আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে এই মহৎ কলার প্রাণবন্ত সৌন্দর্য ও পূর্ণাবয়ব আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে উত্তর-ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য কঠিন ও জটিল তাল-লয়ের সৃষ্টি করে, সে-তাল প্রকাশ করিলে তবলার বোল পদধ্বনিতে শোনা যায়। শুধু তাই নয়, হাবভাব, নিতম্ব ও কটিসঞ্চালন, কটাক্ষাভঙ্গি, স্কন্ধান্দোলন, এক কথায় সর্ব অঙ্গের চালনা ও ভাবপ্রকাশ শুদ্ধমাত্র দর্শকের হৃদয়ে পাশবিক আনন্দদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এইসব নৃত্যে বিকাশপ্ৰাপ্ত আঙ্গিকের সন্ধান মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু বেশির ভাগই হীন ও অশ্লীল।
দক্ষিণে প্রচলিত ভরত নাট্যম শুদ্ধ হিন্দুকলা। ভরত নাট্যে যেসব ‘মুদ্রা’ দ্বারা দেবদেবী, পশুপক্ষী ও বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ করা হয় সেইগুলি এই নৃত্যের মুখ্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। উত্তরের কথক নৃত্যের তুলনায় ভরত নৃত্যে পদসঞ্চালনের কারুকার্য নাই এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গসঞ্চালনও অপেক্ষাকৃত কর্তিত ও সংযত। মালাবারের মোহিনী আট্যম অনেকটা ভারত নাট্যের ন্যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নৃত্য মরণোন্মুখ— সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণের সব কয়টি উচ্চাঙ্গ নৃত্যই কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরাই নাচিয়া থাকে-অতি অল্প বয়সেই বালিকারা পুরুষ পেশাদারের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করে ও বহুবৎসর ব্যাপী কঠিন নিয়ম রীতিমত পালন করিয়া নৃত্যকলায় পারদর্শিনী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব নৃত্যে আজকাল কেবলমাত্র শুষ্ক আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়, শুদ্ধ কলার চিহ্নমাত্র নাই। যে নৃত্য সৃষ্টি করে না, কেবলমাত্র পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, তাহার যে এই গতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি!
আজকাল কথাকলি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও এ-সম্বন্ধে প্রচুর বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে বলিয়া এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন। এদেশের সর্বত্রই নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান অভিনয় করিয়া থাকে; বিভিন্ন প্রদেশে ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। মালাবারে ইহারা কথাকলি নামে পরিচিত।–‘কথা’ অর্থ ‘গল্প’ ও ‘কলি’ অর্থ ‘নাট্য’। কথাকলির অভিনেতারা অন্যান্য প্রদেশের নটনটীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করে না; তাহারা মুক অভিনয় করে, তবলা ও মন্দিরা সহযোগে নাচে ও তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুইজন গায়ক গল্পগুলি গান গাহিয়া শুনায়। মুক্ত আকাশের নীচে অভিনয় হয় ও সূর্যোদয় পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলে। অভিনেতারা বৃহৎ চুনটদার জামাকাপড় পরে ও বিচিত্র প্রসাধনের দ্বারা একপ্রকার অভিনব মুখোশ নির্মাণ করে। কথাকলি নৃত্যের কটাক্ষ, মুখের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার ‘মুদ্রা’র ব্যবহার ও বিশেষত পদদ্বয়ের সম্প্রসারণ দ্বারা নৃত্যকে প্ৰাণদান প্রভৃতি আঙ্গিক অত্যন্ত দুরূহ ও বহুবৎসর ব্যাপী কঠিন সাধনা ব্যতীত এই কলায় দক্ষতা লাভ অসম্ভব। নয় দশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই বালিকাকে নৃত্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হয় ও পূর্ণ যৌবন লাভ না করা পর্যন্ত নর্তকীকে কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া জীবনযাপন করিতে হয়।
কথাকলি নিছক নৃত্য নয়, নৃত্যনাট্যও নয়। বরঞ্চ মুখোশপরা তামাসা-নাচের সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য অধি; নৃত্যকলা ইহাতে স্ফুরিত হয় না। নৃত্যের প্রারম্ভেই যবনিকান্তরালে দুই-একটি আবাহন নৃত্য করা হয় ও তারপর প্রত্যেক শ্লোক বা গান গাওয়া শেষ হইতেই অভিনেতারা চক্রাকারে ‘কলসম’ নৃত্য করে। তারপর স্ত্রী চরিত্রের ‘সরি’ নৃত্য ও রাজহংস বা ময়ুরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।
কথাকলি নৃত্য শক্তি ও তেজঃপ্রধান, কিন্তু অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যে পদসঞ্চালনের যে কারুকার্য ও গতিছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। ইহাতে তাহার অত্যন্ত অভাব। অভিনেত্রীদিগকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও যে কেন তাহাদের নৃত্য এত রূঢ় ও অপক্করূপে প্রকাশ পায়, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা যায় না। কথাকলি গণ্ডিবদ্ধ বলিয়া পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট ও মাঝে মাঝে তাহার বস্তুতান্ত্রিকতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়াই আজ কথাকলি আমাদের কৌতূহল ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সুকুমার কলা হিসাবে এই নৃত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ন্যায় আজ মৃত।
মাত্র কুড়ি বাইশ বৎসর হইল এদেশে নৃত্যকে বিষাক্ত পরিবেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনে স্থান দিবার চেষ্টা করা হইতেছে ও সঙ্গীত চিত্রাঙ্কনের ন্যায় নৃত্যও সুকুমার কলা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। তাই আজকাল সঙ্গীতের মজলিসে, স্কুল-কলেজের আমোদ অনুষ্ঠানে, পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব-আনন্দে নৃত্যচর্চা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে মিলাইয়া কেবলমাত্র তালসংযুক্ত পদসঞ্চালন থাকিলেই তাহা পূর্বের ন্যায় এখনও নৃত্য নামে নন্দিত হয়। সেই নৃত্যকলা এখন ‘ফ্যাশান’ হইয়া দাঁড়াইয়াছে-কোনো রকম শিক্ষা-দীক্ষা না লইয়াই চ্যারিটি-রিলিফ ফান্ডের অজুহাতে যত্রতত্র নৃত্য করা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখনও কি এই সরল তত্ত্বটি বুঝিবার সময় হয় নাই যে নৃত্য অর্থহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্ষেপের মূল্যহীন সমষ্টিমাত্র নহে? এখনও কি দেশবাসী বুঝিবে না যে, নৃত্য অন্যান্য সুকুমার কলার ন্যায় একনিষ্ঠ ও আজীবন সাধনাসাপেক্ষ কলা বিশেষ? অতি অল্পসংখ্যক নর্তক-নর্তকীই এযাবৎ অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন ত্যাগ করিয়া প্রকৃত নৃত্যরসে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। এবং ইহাদের ভিতরেই বা কয়জন সত্যাসত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে নৃত্যের ন্যায় উচ্চাঙ্গের সুকুমার কলায় পারদর্শী হইতে হইলে তাহার প্রতি কী অবিচল নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়? বেশির ভাগই তো দেখিতে পাই দুই-একদিনের ছন্নছাড়া শিক্ষায় দুই একটি নৃত্যেই সন্তুষ্ট। তাহাতে তো শুধু লোক ভুলানো চলে-সে তো কলা নহে। তাই সামান্য যে কয়জন প্রকৃত নৃত্যকলা হিসাবে গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেছেন। তঁহারা সত্যই প্রশংসনীয়। সমাজের বাধাবন্ধ উপেক্ষা করিয়া তাহারা সাহসের ভরে লোকচক্ষুর সম্মুখে নৃত্যকলা দেখাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহারাও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যগত নৃত্য দেখাইয়াই সন্তুষ্ট। তঁহাদের নৃত্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নাই। পেশাদার নর্তকেরা যে দৈন্য বহু সাধনালব্ধ আঙ্গিকের দ্বারা লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তাঁহাদের নৃত্যে তাহা বার বার ধরা পড়ে। ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা যে কাহারও নাই এমন নহে, কিন্তু আছে অতি অল্পসংখ্যক গুণীর ভিতরে। র্তাহারা যে শুধু গভীর সাধনার দ্বারা নৃত্য আয়ত্ত করিয়াছেন এমন নহে, তাহারা যে শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যগত নৃত্য সর্বাঙ্গসুন্দরীরূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও নহে, তীহাদের বিশেষত্ব এই যে, বর্তমান যুগের রুচি অনুযায়ী তাহার নৃত্যের প্রাচীন বিষয়বস্তুকে নূতন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত গুণীর চরম লক্ষ্য তো ইহাও হইতে পারে না; তিনি সৃষ্টিকর্তা, তাহাকে নব নব বিষয়ের কল্পনা করিতে হইবে, নব নব রূপে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে হইবে-জরাজীর্ণ বৃদ্ধাকে নবীনবেশে সজ্জিত করিয়া তিনি কেন বিড়ম্বিত হইবেন? জীবনীশক্তির যে দ্রুত, অবিশ্রান্ত স্পন্দন আমরা আমাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। অতি সনাতন ভাবনা-কামনা একদিন যে রূপ, যে বর্ণ নিয়া প্রকাশিত হইত তাহার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ সংগ্রাম, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের কোথায় যোগসূত্র? সুকুমার কলা কি কখনো মৃত্যুদগ্ধ চিস্তা অনুভূতির অন্ধকূপে প্রাণধারণ করিতে পারে? নৃত্য তো শুধু তাললয়যোগে অঙ্গসঞ্চালন নয়, নৃত্য তো সুচারু পদক্ষেপের নামান্তর নয়; আঙ্গিকের উৎকর্ষ নৃত্য, অঙ্গবিন্যাস দ্বারা সুদৰ্শন আলিম্পন সৃষ্টি করাও নৃত্য নয়। প্রকৃত নৃত্যের চরম আদর্শ আমাদের জীবনের দ্বন্দ্বানুভূতি প্রকাশ করা, সত্য ও সুন্দরকে উন্মোচন করিয়া আমাদের চক্ষুর গোচর করা। জিজ্ঞাসা করি রাধা-কৃষ্ণ, শিব-পার্বতী নৃত্য কি যথেষ্ট নাচা হয় নাই, প্রচুর দেখা হয় নাই? এখনও কি ধর্মের আচ্ছাদনে আবৃত কুসংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করিবার সময় হয় নাই? এ যুগের মানুষের কি নিজস্ব কোনোও অনুভূতি, কোনো দ্বন্দ্ব, কোনো আশা, কোনো আদর্শ নাই? তাহাদের কি কিছুই বক্তব্য নাই-মানবসংসারে চিরন্তন দীপান্বিতা প্ৰজ্বলিত করিবার কোন প্ৰদীপ নাই? বাহির হইয়া আসুক এ দেশের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, মোহমুক্ত হইয়া প্রকাশ করুক তাহাদের আশাঅনুভূতি আপন সবল কণ্ঠে, শুধু কর্মে নয়,-সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে ।।–(শ্ৰীমতী ঠাকুরের গুজরাতি লিখন হইতে অনুদিত)।
মপাসাঁ
বাঙালায় বলি, ‘গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না’, ‘পদ্মার ওপারে বলি,–
‘পীর মানে না দেশে-খেশে,
পীর মানে না ঘরের বউয়ে,’
আর পশ্চিমারা বলেন, ‘ঘরকী মুর্গী দল বরাবর’ অর্থাৎ পরে পোষা মুর্গী মানুষ এমনি তাচ্ছিল্য করে খায়, যেন নিত্যকার ডাল-ভাত খাচ্ছে।
কিন্তু একবার গায়ের কদর পাওয়ার পর আবার যে মানুষ গেঁয়ো যোগী হতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনো প্ৰবাদ আমার জানা নেই। কিন্তু তাই হয়েছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মপাসাঁর বেলায়।
মাস তিনেক পূর্বে মপাসাঁর কয়েকখানা চিঠি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তারি সমালোচনা করতে গিয়ে ফরাসী একাডেমির সদস্য-অর্থাৎ তিনি অতিশয় কেষ্ট-বিষ্টু জন-মাসিয়ো আঁদ্রে বিইঈ (Billy) মপাসাঁ সম্বন্ধে মিঠে-কড়া দু-চারটি কথা বলেছেন।
এক ফরাসী সাহিত্য-প্রচারক নাকি বিইঈকে বললেন, ‘কেন্ত্রিজের ছেলে-মেয়েরা আজকাল যে মপাসাঁ পড়ে, সে শুধু অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল নিয়ে।’ (অর্থাৎ মপাসাঁর যৌন গল্পগুলোই তারা পড়ে বেশি)। উত্তরে বিইঈ বললেন, ‘বিদেশীরা, বিশেষত কেন্ত্ৰিজ অক্সফোর্ডের লোক আজকাল আর মপাসাঁ পড়ে না, তারা পড়ে প্রস্ত, ভালেরি, মালার্মে, র্যাবো। মপাসাঁর কদর এখনো আছে জর্মনি এবং রাশায়। খুদ ফ্রান্সে ছোকরার দল তো মপাসাঁকে একদম পাঁচের বাদ দিয়ে বসে আছে। ভুল করেছে না ঠিক করেছে? কিছুটা ভুল কিছুটা ঠিক-কারণ মপাসাঁ একদিক দিয়ে যেমন অত্যাশ্চর্যকলাসৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে আবার অত্যন্ত যাচ্ছেতাইও লিখেছেন।’
এ সম্পর্কে মপাসাঁর চিঠি প্ৰকাশ করতে গিয়ে সম্পাদক মেনিয়াল(১) বলছেন, ‘আমেরিকার লোকে মপাসাঁ পড়ে উঁচুদরের ক্লাসিক হিসেবে। মপাসাঁর সর্বাঙ্গসুন্দর ভাষাকে সেখানকার ফরাসী পড়ুয়া মাত্রই আদর্শরূপে মেনে নেয়। তাঁর ভাষার স্বচ্ছতার জন্যই (সে স্বচ্ছতার উচ্ছসিত প্ৰশংসা করেছেন আনতোঁল ফ্রাসের মত গুণী আমেরিকাতে মপাসাঁর লেখা উদ্ধৃত করে অন্তত কুড়িখানা পাঠ্য বই বেরিয়েছে।’
উত্তরে বিইঈ সাহেব অবিশ্বাসের সুরে বলেছেন, ‘জানতে ইচ্ছে করে, এখনো কি মার্কিন পাঠক মপাসাঁকে এতটা কদর করে? আর ইংলন্ডের অবস্থা কি? মেনিয়াল তো কিছু বললেন না; আমার মনে হয়, মপাসাঁর লেখাতে যেটুকু খাঁটি ফরাসি ইংরেজ সেটা এড়িয়ে চলে।’
চলতে পারে, নাও চলতে পারে। সে কথা উপস্থিত থাক। এর পর কিন্তু বিইঈ সায়েব যেটা বলেছেন সেটা মারাত্মক। সকলেই জানেন, মপাসাঁ ছিলেন ফ্লবেরের অতি প্রিয় শিষ্য-ফ্লবের তাঁকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়েছিলেন। বিইঈ বলেছেন, ফ্রাবের তার প্রিয় শিষ্যের কোনো দোষই দেখতে পেতেন না। কিন্তু তিনি পর্যন্ত বেঁচে থাকলে মপাসাঁর অত্যধিক (Surabondant = Superabundant) লেখার নিন্দা করতেন।’
এ কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, তবে এ সম্পর্কে হিটলারের একটা মন্তব্য মনে পড়ল। হিটলার বলতেন, ‘আজকালকার ছোকরার বড্ড বেশি বই পড়ে আর তার শতকরা নব্বই ভাগ ভুলে যায়। তার চেয়ে যদি দশখানা বই পড়ে ন’খানা মনে রাখতে পারে, তবে সেই হয় ভালো।‘ মাস্টার হিসেবে আমার জানা আছে, দশখানা বই পড়লে ছেলেরা ভুলে মেরে দেয় ন’খানা। কিম্বা বলতে পারেন, পাঁচ দুগুণে দশের শূন্য নেমে হাতে রাইবে পেন্সিল!
মপাসাঁ যদি তাঁর লেখার ত্রিশ ভাগ কমিয়ে দিতেন, তবে সে ত্রিশ ভাগে কি শুধু তার খারাপ লেখাগুলিই-বিইঈর বিচারে-পড়ত? কাটা পড়ত দুইই। তাহলে অন্তত শতকরা কুড়িটি উত্তম গল্প আমরা পেতুমই না! ইংরেজিতে বলে, টিবের নোংরা জল ফেলার সময় বাচ্চাকেও ফেলে দিয়ে না।’ ফেলা যায় বলেই এ সতর্কবাণী!
ভাল লেখা বার বার পড়ি। খারাপ লেখা একবার পড়ে না পড়লেই হল।
কিন্তু মোদ্দা কথায় আসা যাক।
ইংরেজ, জর্মন, রাশান, স্পেনিশ, এমন কি আরবী, ফারসী বাঙলা, উর্দু নিন এমন কোন সাহিত্য আছে যে মপাসাঁর কাছে ঋণী নয়? ছোট গল্প লেখা আমরা শিখলুম কার কাছ থেকে? উপন্যাসের বেলা বলা শক্ত কে কার কাছ থেকে শিখল, কিন্তু ছোট গল্প লেখা সবাই শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। কিম্বা দেখবেন রাম যদি শ্যামের কাছ থেকে শিখে থাকেন, তবে শ্যাম শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। স্বয়ং রবীন্দ্ৰনাথ মপাসাঁর কাছে ঋণীযদিও জানি অসাধারণ প্রতিভা আর অভূতপূর্ব সৃষ্টিশক্তি ধারণ করতেন বলে রবীন্দ্রনাথ বহুতর গল্পে মপাসাঁকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছেন। গীতিরস ছিল রবীন্দ্রনাথের হস্তস্তলে-মপাসার যেখানে ছিল কিঞ্চিৎ অনটন-তাই ছোট গল্পে গীতিরস সঞ্চার করে তিনি এক নতুন রসবস্তু গড়ে তুললেন, কবিতাতে সুর দিয়ে যে রকম ঐন্দ্ৰজালিক গান সৃষ্টি করেছিলেন।
শেষ কথা, কার ভাণ্ডার থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি চুরি করেছে? যে কোনো একখানা হেজিপোঁজি মাসিক হাতে তুলে নিন। দেখবেন ভালো গল্পটি মপাসাঁর লোপাট চুরি—দেশকলপাত্র বদলে দিয়ে। আর আশ্চর্যামপাসাঁর বেলাই এ জিনিসটা করা যায় সব চেয়ে বেশি, কারণ তাঁর অধিকাংশ গল্পই সব কিছুর সীমানা ছাড়িয়ে যায়।
এত চুরির পরও যাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত তিনি প্ৰাতঃস্মরণীয়।
——-
(১) M. Edouard Mayniai এবং Artine Artinian কর্তৃক প্রকাশিত Correspondence inedite.
রবীন্দ্র সঙ্গীত ও ইয়োরোপীয় সুরধারা
প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যায়, ইয়োরোপ রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনতে পেরেছিল, আর আজ যে ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ বড় একটা করে না তার কারণ কি?
এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সে প্রশ্ন স্বাগত— আমরা, অর্থাৎ বাঙালিরাই রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনি? রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা, নাট্যনিৰ্মাণক্ষমতা, দার্শনিক চিন্তাশক্তি, সার্বভৌমিক ধর্মানুভূতি, ঔপন্যাসিক অন্তর্দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, ঐতিহ্যগত শিক্ষাদান প্রচেষ্টা বৈয়াকরণিক অনুসন্ধিৎসা—সব কিছু মিলিয়ে তার অখণ্ড রূপ হৃদয়মনে আঁকার কথা দূরে থাক, যেখানে তিনি ভারতের তথা পৃথিবীর সব কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তারই সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়েছেন কজন বাঙালি?
কবিতার কথাই ধরা যাক। সেখানে দেখি কেউ কেউ ‘কল্পনা’ ছাড়িয়ে কবির সঙ্গে কল্পলোকে ‘হংসবলাকা’র পাখা মেলতে নারাজ, কেউবা ‘মহুয়া’তে পৌঁছে বঁধুকে, ‘মহুয়া’ নাম ধরে ডেকেই সন্তুষ্ট, আর ‘রোগশয্যায়’ কবিকে সঙ্গ দিতে রাজী অতি অল্প দুঃসাহসী রসজ্ঞ। কাউকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; আমি নিজে গুরুদেবের গদ্যকবিতার রস পাই না। কাজেই আমরা সকলেই পরমানন্দে অন্ধের হস্তীদর্শন করছি-কিন্তু আমাদের চরম সান্ত্বনা, এ সংসারের অধিকাংশ অন্ধ আপনি আপনি যষ্টি ত্যাগ করে বৃহত্তর লোকের ক্ষীণতম আভাস পাওয়ার জন্য অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ উদগ্ৰীব নয়।
এ-কথাও বলা বৃথা যে রবীন্দ্র-কাব্যের সম্পূর্ণ রস পাই আর নাই পাই, তার কাব্যজগতের মূল সুরটি আমরা ধরতে পেরেছি। মনে পড়ছে বিশ্বভারতীর সাহিত্যসভায় এক তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের কাব্যে প্রধান দুটি মিল দেখিয়ে একখানা সরেস প্ৰবন্ধ পড়েছিলেন—বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস উভয়েই বর্ষার ও প্রেমের কবি। প্ৰবন্ধ পাঠ শেষ হলে সভাপতিরূপে কবিগুরু লেখাটির প্রচুর প্রশংসা করে বলেন যে, ‘যদিও মিল দুটি স্বীকার্য তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন এই দুই বস্তু বাদ দিয়ে ভারতীয় কোন কবি কি লিখতে পারতেন?’ রবীন্দ্রনাথ সালঙ্কার আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন,–এতদিন পরে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে তার প্রতিবেদন দেওয়া আমার পক্ষে ‘সাহিত্যিক’ সাধুতার পরিচায়ক হবে না, তবে ভাবখানা অনেকটা এই ছিল যে রাফায়েল মাদোন্না এঁকেছেন, অজন্তাকারও মাতাপুত্র এঁকেছেন কিন্তু দুজনের ভিতর সত্যিকার মুল কতদূর?
অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর যদি এই শ্রেণীরই হয় তবে তার কোনো মূল্য নেই।
(এস্থলে অবান্তর হলেও একটি কথা না বললে হয়তো প্ৰবন্ধলেখকের প্রতি অন্যায় করা হবে। যদিও রবীন্দ্ৰনাথের মতে প্ৰবন্ধটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সপ্রমাণ করে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছিল তবু সভাস্থ আর পাঁচজন সে মত পোষণ করেন নি, এবং বিশ্বভারতীর যে কোনো ছাত্র এ রকম প্ৰবন্ধ লিখতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।)
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার মহত্তম এবং মধুরতম বিকাশ তাঁর গানে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলতেন যে তিনি তাঁর গানে প্রকৃতিকেও হারাতে পেরেছেন এবং সে গর্বটুকু একটা গানে অতি অল্প কথায় প্রকাশ করেছেন :
আজ এনে দিলে, হয়ত দিবে না কাল–
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান।
শুধু কদম ফুল। প্রকৃতির কত নগণ্য সৌন্দর্যবস্তু, মানুষের মত উচ্চা আশা-আকাঙক্ষা, ক্ষুদ্র দুঃখ-দৈন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত স্পর্শমণির স্পর্শে হেমকান্ত সফল পরিপূর্ণতায় অজরামর হয়ে গিয়েছে, এবং ভবিষ্যতে,-ক্যাথলিকদের ভাষায় বলি,-ক্যাননাইজড হয়ে যুগ যুগ ধরে বাঙালির স্পর্শকাতর হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি আকর্ষণ করবে।
অথচ আজকের দিনে এ-কথাও সত্য সে অল্প বাঙালিই রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গানের আড়াইশ গান শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।
তবে কি আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বে প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাই নি? সেকথাও সত্য নয়। আমরা এতক্ষণ বাঙালি যুধিষ্ঠিরকে শুধু তাঁর নরক দর্শন করাচ্ছিলুম এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলুম যে বাঙালির পক্ষেও যদি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণরূপে চেনা এত কঠিন হয় তবে অবাঙালির পক্ষে, বিশেষত সাহেবের পক্ষে-তা তিনি ইংরেজই হোন আর জর্মনই হোন-সম্পূর্ণ অসম্ভব।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ যান। তখন তিনি বিশেষ করে জর্মনীতে রাজাধিরাজের সম্মান পান। সে সম্মানের কাহিনী বিশ্বভারতী লাইব্রেরিতে নানা ভাষায় সযত্নে রক্ষিত আছে।
তারপর রবীন্দ্ৰনাথ আবার জর্মন যান। ১৯৩০ সালে। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ততম গৃহে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এক জয়ন্তী উপলক্ষে সমস্ত জর্মানির বিদ্বজ্জন তখন মারবুর্গে সমবেত; তারা সকলেই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে ধর্ম সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করেন। অধ্যাপক অটো সে বক্তৃতার জর্মন অনুবাদ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রচনা পাঠ শুনেছিল এবং পাঠ শেষ হলে যে উচ্ছসিত প্রশংসাধ্বনি উঠেছিল, তার তুলনা দেবার মত ভাষা আমার নেই।
সেদিন বিবেলবেলা মারবুর্গের পুস্তকবিক্রেতাদের দোকানে গিয়ে অনুসন্ধান করলুম, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন পুস্তকের জর্মন অনুবাদ পাওয়া যায়। নির্ঘণ্ট শুনে আশ্চর্য হলুম–গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার, চিত্রা, ডাকঘর, সাধনা এবং নেশানালিজম! মাত্র এই কখানি বই নিয়ে আর ইংরেজি ভাষায় একটি বক্তৃতা শুনে জর্মনরা এত মুগ্ধ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং এখনো আছে যে ইংরেজি বা জর্মনে এই কখানা বই পড়ে রবীন্দ্রনাথের আসল মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।
তখনই আমার বিশ্বাস হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জর্মনির এই উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হবে না। গীতাঞ্জলির ধর্মসঙ্গীত জর্মন মনকে চমক লাগাতে পারে, গার্ডেনারের প্রেমের কবিতাও জাদু বানাতে পারে, সাধনার রচনাও বিদ্যুৎশিখার মত ঝলকাতে পারে। কিন্তু এসব দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতর এবং শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির অনুবাদ অপরিহার্য।
কিন্তু কোনো ব্যাপক অনুবাদকার্য কেউ হাতে তুলে নেন নি। তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে অনেক গবেষণার প্রয়োজন। উপস্থিত শুধু সব চেয়ে বড় দুঃখটা নিবেদন করি।
রবীন্দ্রনাথের গানের মত হুবহু গান জর্মনে আছে এবং সেগুলি জর্মনদের বড় প্রিয়। এগুলোকে লীডার’ বলা হয় এবং শুধু লীডার গাইবার জন্য বহু জর্মন গায়ক প্রতি বৎসর প্যারিস, লন্ডন যায়। এসব লীডারের কোনো কোনো গানের কথা দিয়েছেন গ্যোটের মত কবি, আর সুর দিয়েছেন বেটোফোনের মত সঙ্গীতকার।
আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গানে গ্যোটে বেটোফেনের সমন্বয়। একাধারে এই দুই সৃজন পন্থার সম্মেলন হয়েছিল বলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত জর্মন লীডারের চেয়ে বহুগুণে শ্ৰেষ্ঠ। অনুভূতির সূক্ষ্মতা, কল্পনার প্রসার, এবং বিশেষ করে সুর ও কথার অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত অর্ধনারীশ্বর পৃথিবীর কোনো গান বা ‘লীডার’ জাতীয় সৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হন। নি—রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে রকম হয়েছে।
বাঙালিকে বাদ দিলে রবীন্দ্ৰ-সঙ্গীতের প্রকৃত মূল্য একমাত্র জর্মনিই ঠিক বুঝতে পারবে।
কোনো ব্যাপক অনুবাদ তো হ’লই না, এমন কি রবীন্দ্রনাথের গানও জর্মন-কণ্ঠে গীত হ’ল না।
কাজেই ‘সাত দিনের ভানুমতি’ আট দিনের দিন কেটে গেল। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেদিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মত অনুবাদক কবি ইয়োরোপে জন্মাবেন সেদিন ইয়োরোপ
‘চিনে নেবে চিনে নেবে তারে।’।।
শমীম
আমার বন্ধু শামীম মারা গিয়েছে। শামীম। এ-সংসারে কোনো কীর্তি রেখে যেতে পারে নি, যার জন্যে লোকে সভাস্থলে কিংবা কাগজে শোক প্রকাশ করবে। তার আত্মজন এবং নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাকে কেউ বেশিদিন স্মরণ করবে না।
তার কথা আপনাদের জোর করে শোনাবার অধিকার আমার নেই, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, শামীম কোন কীর্তি রেখে যেতে পারে নি। তবু যে কেন তার সম্বন্ধে লিখছি, তার কারণ সে আমার বন্ধু, আর তাই আশা, আমার বহু সহৃদয় পাঠক সেই সূত্রে তাকে মেহের চোখে দেখবেন, এবং বহু দেশ দেখবার পর বলছি, ওরকম সচ্চরিত্র ছেলে আমি কোথাও দেখি নি।
শামীম আমার ছেলের বয়সী। তার জন্মের প্রায় প্রথম দিন থেকেই আমি তাকে চিনি। আর এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে সে জন্মাল, আর সে সৌন্দর্য দিন দিন এমনি বাড়তে লাগল যে, বাড়িতে যে আসত, সেই ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারত না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল, কী বিনয়নম্র ভদ্রসংযত ব্যবহার এবং পরদুঃখকাতর হৃদয়ভগবান তাকে দিয়েছেন। আমি নিশ্চয়ই জানি বাড়ির ভিতরে বাইরে এমন কেউ ছিল না যে শমীমের উপর বিরক্ত হয়েছে কিংবা র্যাগ করেছে।
কিন্তু তবু বলব, শামীম মন্দ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিল।
ধরা পড়ল সে সন্ন্যাস রোগে ভুগছে। সন্ন্যাসের চিকিৎসা আছে কি না জানি নে, কিন্তু একথা জানি, তার পিতা (আমার অগ্রজ-প্রতিম) চিকিৎসক হিসেবে আর আমরা পাঁচজনে বন্ধুবান্ধব হিসেবে তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি করি নি। আর মায়ের সেবা সে কতখানি পেয়েছিল, সেকথা কি বলব? সর্বকনিষ্ঠ চিররুগ্ন কোন ছেলেকে তার মা হৃদয় উজাড় করে সেবা-সুশ্রুষা করে না?
ভগবান এতেও সন্তুষ্ট হলেন না,-তাকে দিলেন মারাত্মক টাইফয়েডু জুর। আমি দেশে ছিলুম না, ফিরে এসে দেখি জুর যাবার সময় শমীমের একটি চোখ নিয়ে গিয়েছে। আমি অনেক দুঃখকষ্ট অবিচার-অত্যাচার দেখেছি, সহজে কাতর হই নে, কিন্তু শমীমের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যে আঘাত পেয়েছিলুম। সে আঘাত যেন আমার চেয়ে দুর্বল লোককে ভগবান না দেন।
শমীমের বাপ খুড়া ঠাকুর্দা সকলেই গভীর প্রকৃতির-শামীমও ছেলেবেলা থেকে শাস্তস্বভাব ধরত, এখন সে ক্রমে ক্ৰমে গভীর হতে লাগল। পড়াশোনা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কখনো যে করতে পারবে সে ভরসা ক্রমেই ক্ষীণ হতে লাগল। হয়তো তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করত-আশ্চর্য কি, যে ছেলে অল্পবয়সে লেখাপড়ায় সকলের সেরা ছিল তার সব লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো মর্মদ্ভদ ব্যাপার কি হতে পারে?
বিশ্বাস করবেন না, ঐ গাভীর্যের পিছনে কিন্তু তার ছিল প্রচুর রসবোধ। আমাকে খুশি করবার জন্য সে আমাদের বাড়ি-নং পার্ল রোড সম্বন্ধে একটি রচনা লেখে। তাতে আমাদের সকলের রসময় (অনেকটা আইরিশ ধরনের হিউমার) বর্ণনার পর ছিল উপরের তলায় তার দাদামশায়ের বর্ণনার ফিনিশিং টাচু। দাদামশায় আসলে কুষ্ঠিয়ার লোক, ‘এটা’ ‘সেটা’ না বলে বলেন ইডা’, ‘সিডা’, আর বুড়োমানুষ বলে সমস্ত দিন বাড়ির এঘর ওঘর করে বেড়ান। তার বর্ণনা শামীম দিল এক লাইনে—’আর দাদামশাই তো সমস্ত দিন ‘ইডা’ ‘সিডা’ নিয়ে আছেন।
শমীমের বড় ভাই শহীদ তখন প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম হাসি। খানার টেবিলে একদিন জল্পনাকল্পনা হচ্ছে, একটা চড়ুই-ভাত করলে হয় না? শহীদ গভীর হয়ে বসে আছে–আমি শুধালুম, ‘তুমি আসছে তো?’ শহীদ বলল, ‘না।’
শামীম বলল, ‘ও আসবে কেন? আমরা তো ‘হাসি’ না।’
অর্থাৎ তার ডার্লিং ‘হাসি’ তো আমাদের সঙ্গে চড়ুইভাতে আসবে না এবং আহা, শহীদ কতই না Jolly chap–আমরাই শুধু গম্ভীর।
কিন্তু আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করত। তার পরোপকার করার প্রচেষ্টা। ৪৭-এর দাঙ্গার সময় আমাদের বাড়িতে প্রায় সত্তর জন হিন্দু নরনারী আশ্রয় নেন-আমি তখন দক্ষিণে— ফিরে এসে শুনি গুণ্ডারা বাড়ি আক্রমণ করেছিল, শামীম নিৰ্ভয়ে এদের সেবা করেছে; আমি আশ্চর্য হই নি।
তার পর ৫০ সনে হোলির কয়েকদিন আগে যখন সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে বিস্তর মুসলমান নরনারী এসে আমাদের পাড়ায় আশ্রয় নিল তখন শামীম তার মা, বাবা, বোনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সেবা করল, তার বাবার ডিসপেনসারিতে বসে রুগীদের জন্য ওষুধ তৈরি করাতে, ইনজেকশন-ভেকসিনেশন দেওয়াতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করলে। পৃথিবীর সবাই শামীমকে ভুলে যাবে কিন্তু দু-একটি আর্ত হয়তো এই সুহাস, সুভাষ, প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে মনের কোণে একটুখানি ঠাই দেবে।
সেই সময়ে দিল্লীর এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাদের এবং পাড়ার মুসলমানদের অনেক সাহায্য করেন। আমরা স্থির করলুম, দিল্লীর লোক, একে নিমন্ত্রণ করে কোর্মা-পোলাও খাওয়াতে হবে। সব ঠিক, এমন সময় শামীম তার মাকে গিয়ে বললে, ‘এই দুদিনে লোকে খেতে পাচ্ছে না, আর তোমরা দাওয়াত করে খাওয়াচ্ছ কোর্মা-পোলাও! আমি তা হলে খাব না। যদি নিতান্তই খাওয়াতে হয়, তবে খাওয়াও আমরা যা রোজ খাই।’
আমরা মামুলী খানাই পরিবেশন করেছিলুম।
***
খবর পেলুম, শমীম ট্রেনের সামনে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি কিছুই ভাবতে পারছি নে। এত সহৃদয়, পরোপকারী ছেলে বুঝতে পারল না যে তার মা, বাপ, খুড়ো, ভাই, বোন, আমাকে, তার বন্ধু শুকুরকে এতে কতখানি আঘাত দেবে?
শিক্ষা-সংস্কার
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করা হইবে এই রকম একটি খবর শুনিতে পাইলাম।
পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া এই বিষয়ে নানা তর্ক নানা আলোচনা করিবেন; সেই সব পণ্ডিতের নামাবলীতে দেশবিদেশের নানা ডিগ্ৰী নানা উপাধির লাঞ্ছনা অঙ্কিত থাকিবে; নানা ভাষায় নানা কণ্ঠে তাহারা জ্ঞানগর্ভ মতামত প্ৰকাশ করবেন। সেখানে আমাদের ক্ষীণ নেটিভ কণ্ঠ পৌঁছবে এমন দুরাশা আমরা করি না। আমাদের প্রধান দোষ অবশ্য যে আমরা ‘ওল্ড ফুলজ’ ‘ধর্মপ্ৰাণ’; আমাদের যুক্তিতর্ক ধর্মশাস্ত্ৰ হইতে সঞ্চয় করি, সেগুলি এযুগে বরবাদ রদ্দি জঞ্জাল। কিন্তু আমরা নাচার। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, যে মূলা খাইয়াছে তাহার ঢেকুরে মূলার গন্ধ থাকিবেই, আমরা মূলা’ না খাইয়া থাকিলেও জানি যে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে ‘মূলের অনুসন্ধান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শুনিতে পাই সায়েবরাও নাকি তাই করেন—
দেশে যখন ধনদৌলত পর্যাপ্ত ছিল তখন বহু লোক তীর্থ করিতে যাইতেন এবং বহু পণ্ডিতের এই ধারণা যে তাবৎ উত্তর ভারতে রেলগাড়ি প্রচলিত হইবার পূর্বেও যে ভাঙাভাঙা হিন্দি দিয়া কাজ চালানো যাইত তাহার কারণ যাত্রীদের তীর্থ পরিক্রমা। দেবীর ব্ৰহ্মরন্ধ পীঠ বেলুচিস্থানের হিঙ্গুলা হইতে বামজঙ্ঘা পীঠ শ্ৰীহট্ট পর্যন্ত বহু বহু যাত্রী বহু যুগ ধরিয়া গমনাগমন করিয়াছেন, বহু ভাষার বহু শব্দের আদান-প্ৰদান সংমিশ্রণের ফলে পণ্ডিতজন নিন্দিত একটি চলতি ভাষা যুগ যুগ ধরিয়া রূপ পরিবর্তন করিয়া অধুনা হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত। সে যাহাই হোক, এই অবদানের স্মরণে তীর্থযাত্রীদের প্রশংসা করিবার সদুদেশ্য লইয়া ব্যক্ষ্যমাণ আলোচনা নিবেদন করিতেছি না।
তীর্থে পুণ্যসঞ্চয় হইত। কিনা সে তর্ক অধুনা নিৰ্ম্মফল, কিন্তু এ বিষয়ে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, জ্ঞান সঞ্চয় হইত, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইত, সঙ্কীর্ণতা হ্রাস পাইত এবং নানা বর্ণ, নানা জাতি, নানা আচার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়াও যাত্রী হৃদয়ঙ্গম করিত ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ। আবার বলি, নানা পার্থক্য নানা বৈষম্যের গন্ধধূপধূম্রের পশ্চাতে ভারতমাতার সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি প্রস্ফুটিত হইত। গ্রামের বৈচিত্র্যহীন সমাজে ফিরিয়া আসিয়াও তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত সেই সুস্পষ্ট আলেখ্য।
শিক্ষার এক মূল অঙ্গ ছিল তীর্থভ্রমণ, দেশভ্রমণ বলিলে একই কথা বলা হয়।
প্রশ্ন এই, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো অজস্র ডিগ্রি প্রতি বৎসর অকৃপণভাবে বর্ষণ করেন, কিন্তু কখনো তো বিদ্যার্থীকে বার্ষিক পরিক্রমার সময় জিজ্ঞাসা করেন না, ‘তুমি দেশভ্ৰমণ করিয়াছ, ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ হৃদয়ে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছ?’
বোধ হয় করা হয় না, তাই যখন সাধারণ বাঙালি গ্রাজুয়েট লিলুয়ার টিকিট কাটে তখন বলিয়া বেড়ায়, ‘ভাই, কি আর করি, হাওয়া বদলাইতেই হয়, পশ্চিম চলিলাম।’
অসহিষ্ণু পাঠক বলিবেন, কী বিপদ! বিশ্ববিদ্যালয় কি বুকিং আপিস যে তুমি বাতায়নস্থ হইলেই তোমাকে সস্তায় বিদেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন?
নাই বা দিলেন, কিন্তু এমন বন্দোবস্ত কি সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, বাঙালি ছেলে ছয় মাস এলাহাবাদে পড়িল, আরো ছয় মাস লাহোরে এবং সর্বশেষ তিনি বৎসর কলিকাতায়? নিন্দুকে বলে যে, কলেজের ছেলেরা নাকি প্রায় দুই বৎসর গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ায়, শেষের চারি মাস, তিন মাস, অবস্থাভেদে দুই মাস নোট মুখস্থ করিয়া পাস দেয়। তবেই জিজ্ঞাসা, চারি বৎসরের এক বৎসর অথবা এম.এ. পাসের জন্য ছয় অথবা সাত বৎসরের দুই অথবা তিন বৎসর যদি কোনো ছেলে প্রদেশে প্রদেশে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়ার্থে (সে শতকরা এক শত নাই হউক) তীর্থভ্ৰমণ অর্থাৎ এই কলেজ সেই কলেজ করে, তবে কি পাপ হয়?
এমন কি একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও নাই যেখানে তাবৎ ভারতের ছেলে অধ্যয়ন করিতে সমবেত হয়, একে অন্যকে চিনিতে পারে? (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আলীগড়ে ঈষৎ হয়, কিন্তু নানা কারণে এস্থলে তাহার আলোচনা আজ আর করিব না) অথচ সংস্কৃত পড়িবার জন্যে ভারতবর্ষের সর্বপ্রদেশের ছাত্র কাশীর চতুষ্পাঠীতে সমবেত হয়, মুসলমান ছাত্র দেওবন্দ যায়। (বিশ্বভারতীর কথা তুলিলাম না, কারণ সরকারি ছাপ লাইতে হইলে সেখানকার ছাত্রকে এখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খিড়কি দরজা দিয়া ঢুকিতে হয়)।
অবিশ্বাসী পাঠক বলিবেন, কথাটা মন্দ শুনাইতেছে না, তবে ঠিক সাহস পাইতেছি। না। অন্য কোনো দেশে কি এ ব্যবস্থা আছে?’ ‘হোমো’র অর্থাৎ সদাশয় সরকারের দেশের কথা বলিতে পারি না এবং তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, কারণ শুনিয়াছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি স্থিতি নাকি ইস্ট্রন হ্যারোর ক্ৰীড়াভূমিতে। তাই যদি হয়, তবে দেব। পতঞ্জলির ভাষায় বলি, ‘হেয়ং দুঃখমনোগতম। স্বরাজ পাইয়া বিদেশে অপ্রতিহতভাবে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিবার কুমতি ভারতের যেন কদাচ না হয়; তাহাতে পরিণামে যে দুঃখ পাইতে হইবে তাহা পূর্ব হইতেই বৰ্জনীয়।
কিন্তু ফ্রান্সে আছে, জর্মনীতে আছে, সুইটজারল্যান্ডে আছে, অস্ট্রিয়ায় আছে, তাবৎ বলকানে আছে, অথবা ১৯৩৯ পর্যন্ত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলকান রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর শত শত ছাত্র বার্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, জিনিভা যাইত, এক বৎসর দুই বৎসর নানা কলেজ নানা দেশ ঘুরিয়া পুনরায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গিয়ে বাড়ির বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস দিত, বিদেশের টার্ম স্বদেশে গোনা হইত, আর দেশের অভ্যন্তরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তো কথাই নাই। এমন জর্মন ছেলে কস্মিনকালেও খুজিয়া পাইবেন না যে ঝাড়া পাঁচ বৎসর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করিয়া পদবী লইয়াছে। হয়ত উত্তরায়ণ কাটাইয়াছে রাইনল্যান্ড, কলোনে অথবা হাইডেলবের্গে—দক্ষিণায়ন কীল অথবা হামবুর্গে, তার পরের বৎসর মুনিকে ও সর্বশেষ দুই বৎসর স্বপূরী কোনিগসবের্গে। শুধু তাঁহাই নহে। দেশের এক প্রান্তের ছাত্র যাহাতে অন্য প্রান্তে যায় তাহার জন্য রেল কোম্পানি তাহাকে সিকি ভাড়ায় লইয়া যাইতে বাধ্য। ছুটির সময় যখন বাড়ি যাইবে, ফিরিয়া আসিবে, তাহার জন্যও সিকি ভাড়া।
কিন্তু আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। কারণ স্মরণ আছে, শান্তিনিকেতনের ননকলেজেট হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ. পাস করা একটি গুজরাতী ছেলের বাসনা হয় এম.এ. বোম্বাই হইতে দিবে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন নামঞ্জর করিলেন, কারণ সে কলকাতার নন-কলেজেন্ট! কর্তাদের বুঝাইবার বিস্তর প্রয়াস করিলাম যে কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের নন-কলেজেট বহু কলেজেটের অপেক্ষা শ্রেয়, অন্তত বিশ্বভারতী কলেজ অনেক মার্কামারা সফরীপ্রোক্ট কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী ধারণ করে, কিন্তু অরণ্যে রোদন।
ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কি অপূর্ব বিশ্বপ্ৰেম, সহযোগিতা!
শ্রমণ রিয়োকোয়ান
বাস্তুবাড়ি আমূল ভস্মীভূত হওয়ার পরমুহূর্তেই ক্ষতির পরিমাণটা ঠিক কতদূর হয়েছে অনুমান করা যায় না। যেমন যেমন দিন যায়, এটা ওটা সেটার প্রয়োজন হয় তখন গৃহস্থ আস্তে আস্তে বুঝতে পারে তার ক্ষতিটা কত দিক দিয়ে তাকে পঙ্গু করে দিয়ে গিয়েছে।
ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। আগুন নিবেছে বলে উপস্থিত আমরা সকলেই ভারী খুশি কিন্তু ক্ষতির খতিয়ান নেবার সময়ও আসন্ন। যত শীঘ্র আমরা এ-কাজটা আরম্ভ করি ততই মঙ্গল।
ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অহরহ সচেতন হচ্ছি কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যলোকে আমাদের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন। এখনো আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি নি। অথচ নূতন করে সব কিছু গড়তে হলে যে আত্মবিশ্বাস, আত্মাভিমানের প্রয়োজন হয় তার মূল উৎস সংস্কৃতি এবং বৈদগ্ধ্যলোকে। হটেনটটুদের মত রাষ্ট্রস্থাপনা করাই যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কোন প্রকার অনুসন্ধান করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি আর পাঁচটা সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রের সঙ্গে। কঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার বাসনা আমাদের মনে থাকে। তবে সে প্রচেষ্টা ‘ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ’।
আত্মাভিমান জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সে-ও একদিন উত্তমণ ছিল, ব্যাপক অর্থে সে-ও মহাজনরূপে বহু দেশে সুপরিচিত ছিল।
কোন দেশ কার কাছে কতটা ঋণী, সে তথ্যানুসন্ধান বড় বড় জাল পেতে আরম্ভ হয় গত শতাব্দীতে। ভৌগোলিক অন্তরায় যেমন যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে লঙ্ঘন করা সহজ হতে লাগল, অন্যের ইতিহাস পড়বার সুযোগও তেমনি বাড়াতে লাগল। কিন্তু সে-সময়ে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্ত, ইংরেজের সম্মোহন মন্ত্রের অচৈতন্য অবস্থায় তখন সে যা বলেছে আমরা তাই বলেছি, সে যা করতে বলেছে তাই করেছি।
আমাদের কাছে কে কে ঋণী সে-কথা বলার প্রয়োজন ইংরেজ অনুভব করে নি, আমরা যে তার কাছে কত দিক দিয়ে ঋণী সে কথাটাই আমাদের কানের কাছে অহরহ ট্যাটরা পিটিয়ে শুনিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ ছাড়া আরো দু-চারটে জাত পৃথিবীতে আছে, এবং ইংরেজই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভুবনবরেণ্য মহাজন জাতি এ-কথা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়, এমন কি ইংরেজ যার উপর রাজত্ব করেছে। সে যে একদিন বহু দিক দিয়ে ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশি সত্য ছিল সে-কথাটা প্রচার করতেও তাদের বাধে না। বিশেষ করে ফরাসি এবং জর্মন এই কর্মটি পরমানন্দে করে থাকে। কোনো নিরপেক্ষ ইংরেজ পণ্ডিত কখনো জন্মান নি, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে দরদ দিয়ে ভারতবাসীকে ‘তোমরা ছোট জাত নও’ এ-কথাটি বলতে ইংরেজের চিরকালই বেধেছে।
তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা খবর পেলুম যে চীন ও জাপানের বহুলোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম চীন ও জাপানের আত্মবিকাশ বহু দিক দিয়ে যুগ-যুগ ধরে সাহায্য করেছে, তবু সেই গানের ভিতর দিয়ে আমরা এঁদের সঙ্গে নূতন কোনো যোগসূত্র স্থাপনা করতে পারলুম না। এমন সময় এসেছে, চীন ও জাপান যে-রকম। এ-দেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে অধিকতর সংখ্যায় আসবে ঠিক তেমনি আমাদেরও খবর নিতে হবে চীন এবং জাপানের উর্বর ভূমিতে আমাদের বোধিবৃক্ষ পাপী-তাপীকে কি পরিমাণ ছায়া দান করেছে।
এবং এ-কথাও ভুললে চলবে না যে প্রাচ্যলোকে যে তিনটি ভূখণ্ড কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে যশ অর্জন করেছে তারা চীন ভারতবর্ষ ও আরব ভূমি। এবং শুধু যে ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ আরব ও চীন ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে তা নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার দিক থেকেও আমরা এই দুই ভূখণ্ডের সঙ্গমস্থলে আছি। এক দিকে মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা এ-দেশে এসে আমাদের শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছে, আবার আমাদের বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে আমরা চীন-জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে আর্য হয়েও এক দিকে যেমন সেমিতি (আরবী) জগতের সঙ্গে তার ভাবের আদান প্ৰদান চলে, তেমনি চীন-জাপানের (মঙ্গোল) শিল্পকলা চিন্তাধারার সঙ্গেও সে যুক্ত হতে পারে। অথচ চীন আরব একে অন্যকে চেনে না।
তাই পূর্ব-ভূখণ্ডে যে নবজীবন সঞ্চারের সূচনা দেখা যাচ্ছে, তার কেন্দ্ৰস্থল গ্ৰহণ করবে। ভারতবর্ষ। (ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টিবিন্দু থেকে আমাদের লক্ষপতিরা এ তথ্যটি বেশ কিছুদিন হল হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন-জাপান হাট থেকে সরে যেতেই অহমদাবাদ ডাইনে, পারস্য-আরব বঁীয়ে জাভা-সুমাত্রাতে কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেছে) ভৌগোলিক ও কৃষ্টিজাত উভয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যদি আপন আসন গ্ৰহণ না করে তবে দোষ ভগবানের নয় ।
উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মৌলভী-মৌলানারা আরবী-ফারসী জানেন। এঁরা এত দিন সুযোগ পান নি—এখন আশা করতে পারি, আমাদের ইতিহাস-লিখনের সময় ওঁরা ‘আরবিকে ভারতের দান’ অধ্যায়টি লিখে দেবেন ও যে স্থপতিকলা মোগল নামে পরিচিত তার মধ্যে ভারতীয় ও ইরান-তুর্কী কিরূপে মিশ্রিত হয়েছে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন।।
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা চীন এবং জাপানের ভাষা জানি নে। (বিশ্বভারতীর ‘চীন-ভবনে’র দ্বার ভালো করে খুলতে হবে, এবং সেই চীনা-ভবনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে চীন সভ্যতার অধ্যয়ন আলোচনা আরম্ভ করতে হবে।)
জাপান সম্বন্দে আমাদের কৌতূহল এতই কম যে জাপানে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। (তাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বীরভদ্র রাও চিত্র যখন তাঁর শিল্পী’ কাগজে জাপানে সংগৃহীত ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন প্রকাশ করেন তখন অল্প পাঠকই সেগুলো পড়েন। বিশ্বভারতীর আরেক প্রাক্তন ছাত্র শ্ৰীমান হরিহরণ সাত বৎসর জাপানে থেকে উৎসাহের অন্ত নেই।–তার স্ত্রীও জাপানী মহিলা-কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিদ্যার্থী। তার কাছে উপস্থিত হয় নি।)
বক্ষ্যমাণ প্ৰবন্ধ-লেখক জাপানী ভাষা জানে না। কিন্তু তার বিশ্বাস, জাপান সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল জগাবার জন্য ইংরিজি এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা বই দিয়ে যতটা সম্ভবপর ততটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। জাপানী ছাড়া অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধে ভুল থাকার সম্ভাবনা প্রচুর, তাই প্ৰবন্ধ-লেখক গোড়ার থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।
ভারতবর্ষীয় যে-সংস্কৃত চীন এবং জাপানে প্রসারলাভ করেছে সে-সংস্কৃতি প্রধানত বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষীয় তথা চৈনিক বৌদ্ধধর্ম ও জাপানী বৌদ্ধধর্ম এক জিনিস নয়—তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বর এক প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেক ধর্মই প্রসার এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বাতাবরণের ভিতর নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। জেরুজালেমের খ্রিস্টধর্ম ও প্যারিসের খ্রিস্টধর্ম এক জিনিস নয়, মিশরী মুসলিমে ও বাঙালি মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।
জাপানে যে-বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত লাভ করেছে সে—ধৰ্মও দুই দিক থেকে চর্চা করতে হবে। প্রথমত, জাপানীতে অনুদিত ও লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ,–এ কর্মকরবেন পণ্ডিতেরা, এবং এঁদের কাজ প্রধান গবেষণামূলক হবে বলে এর ভিতর সাহিত্য-রস থাকার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, জাপানী শ্রমণ-সাধু-সন্তদের জীবনী-পাঠ। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়লে সে-সব জীবনী নিয়ে বাঙলায় উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।
অধ্যাপক য়াকব ফিশারের লেখা বৌদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ানের জীবনী পড়ে আমার এবিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। অধ্যাপক ফিশার জাতে জর্মন, রিয়োকোয়ান জাপানী ছিলেন,-কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বইখানি লেখা হয়েছে বলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে। পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার সামান্য কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এ-দেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করতে পারে নি। বইখানি ইংরিজিতে লেখা, নাম Dew drops on a Lotus Leaf। আর কিছু না হোক, নামটি আমাদের কাছে অচেনা নয়-নিলিনীদল-গতজলমতিতরলং’ বাক্যটি আমাদের মোহাবস্থায়ও আমরা ভুলতে পারি নি। শঙ্করাচার্য যখন ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ’ আখ্যায় নিন্দিত হয়েছেন তখন হয়তো জীবনকে পদ্মাপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় দেখার উপমাটাও তিনি বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছেন।
বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর
–খাটে, ছেলে যারা মধুর স্বপ্ন দেখে–
থাকিতে আমরা নেই তো অরুচি কোনো।
তবুও এ-কথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নির্জনতার মাঝে
–শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা–
সেইখানে মম জীবন আনন্দঘন।।
শ্রমণ রিয়োকোয়ানের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি দিয়ে অধ্যাপক ফিশার তাঁর রিয়োকোয়ানচরিতের অবতরণিকা আরম্ভ করেছেন।
খ্যাতি শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে শ্রমণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তাঁর বাসনা হয়েছিল, শ্রমণের কাছ থেকে ধর্মশিক্ষা গ্ৰহণ করবেন।
মাকিনোর দূত রিয়োকোয়ানের কুঁড়েঘরে পৌঁছাবার পূর্বেই গ্রামের লোক খবর পেয়ে গিয়েছিল যে স্বয়ং মাকিনো রিয়োকোয়ানের কাছে দূত পাঠাচ্ছেন। খবর শুনে সবাই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কুটিরের চারদিকের জমি বাগান সব কিছু পরিষ্কার করে দিল।
রিয়োকোয়ান ভিনগাঁয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন কুঁড়েঘরের চতুর্দিক সম্পূর্ণ সাফ। মাকিনোর দূত তখনো এসে পৌঁছয় নি। রিয়োকোয়ানের দুই চোখ জলে ভরে গেল, বললেন, ‘হায় হায়, এরা সব কি কাণ্ডটাই না করেছে। আমার সব চেয়ে আত্মীয় বন্ধু ছিল বিবি পোকার দল। এই নির্জনতায় তারাই আমাকে গান শোনাত। তাদের বাসা ভেঙে ফেলা হয়েছে হায়, তাদের মিষ্টি গান আমি আবার শুনব কবে কে জানে?’
রিয়োকোয়ান বিলাপ করছেন, এমন সময় দূত এসে নিমন্ত্রণপত্র নিবেদন করল। শোকাতুর শ্রমণ উত্তর না দিয়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখে দূতকে দিলেন,
আমার ক্ষুদ্র কুটীরের চারি পাশে,
বেঁধেছিল বাসা ঝরা পাতা দলে দলে—
নৃত্যচটুল, নিত্য দিনের আমার নর্ম্য-সখা
কোথা গেল সব? আমার আতুর হিয়া
সান্ত্বনা নাহি মানে।
হায় বলে মোর কি হবে উপায় এবে
জ্বলে গিয়ে তারা করিত যে মোর সেবা,
এখন করিবে কেবা?
ফিশার বলেন, দূত বুঝতে পারল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।
আমরা বলি, তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? আমাদের কবি, জাপানের কবি এবং ঝরা পাতার স্থান তো জাগীরদারের প্রাসাদকাননে হতে পারে না। রবীন্দ্ৰনাথ গেয়েছেন :
ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজিলে।(১)
ফিশার বলেন, এই জাপানী শ্ৰমণ, কবি, দার্শনিক এবং খুশখৎকো(২), তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান।
রিয়োকোয়ান বহু বৎসর ধরে জাপানের কাব্যরসিক এবং তত্ত্বান্বেষীগণের মধ্যে সুপরিচিত, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়ায় মাত্র বৎসর ত্ৰিশ পুর্বে। যে প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তার প্রব্রজ্যাভূমিতে তিনি কিংবদন্তীর রাজবৈদ্য তাৎসুকিচি ইরিসওয়া বলেন, ‘আমার পিতামহী মারা যান। ১৮৮৭ সনে। তিনি যৌবনে রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তার সম্বন্ধে অনেক গল্প আমাকে বলেছেন।’
রিয়োকোয়ানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯১১ সনে প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। স্বয়ং হকুওসাই সে পুস্তকের জন্য ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। তার প্রায় পাঁচিশ বৎসর পর রিয়োকোয়ানের প্রিয়া শিষ্যা ভিক্ষুণী তাইশিন রিয়োকোয়ানের কবিতা থেকে ‘পদ্মাপত্রে শিশিরবিন্দু নাম দিয়ে একটি চয়নিক প্রকাশ করেন। রিয়োকোয়ানকে কবি হিসাবে বিখ্যাত করার জন্য ভিক্ষুণী তাইশিন এ চয়নিক প্রকাশ করেন নি। তিনিই তাকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশি-আর যে পাঁচজন তাঁকে চিনতেন, তাদের ধারণা ছিল তিনি কেমন যেন একটু বেখাপ্লা, খামখেয়ালী ধরনের লোক, যদিও শ্রমণ হিসাবে তিনি অনিন্দনীয়। এমনকি রিয়োকায়নের বিশিষ্ট ভক্তেরাও তাকে ঠিক চিনতে পারেন নি। তাদের কাছে তিনি অজ্ঞেয়, অমর্ত্য সাধক হয়ে চিরকাল প্ৰহেলিকা রূপ নিয়ে দেখা দিতেন। একমাত্র ভিক্ষুণী তাইশিনই রিয়োকোয়ানের হৃদয়ের সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন, চয়নিক প্রকাশ করার সময় তার একমাত্ৰ উদ্দেশ্য ছিল, সর্বসাধারণ যেন তার কবিতার ভিতর দিয়ে তার মহানুভব হৃদয়ের পরিচয় পায়।
এ-মানুষটিকে চেনা কারো পক্ষেই খুব সহজ ছিল না। তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন কবিতা লিখে, ফুল কুড়িয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের রাস্তার উপর খেলাধুলা করে। তাতেই নাকি পেতেন। তিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ। খেলার সাখী না পেলে তিনি মাঠে, বনের ভিতর আপন মনে খেলে যেতেন। ছোট ছোট পাখি। তখন তার শরীরের উপর এসে বসলে তিনি ভারী খুশি হয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তেন, মদ পেলে খেতে কসুর করতেন না, আর নাচের দলের সঙ্গে দেখা হলে সমস্ত বিকেল-সন্ধ্যা তাদের সঙ্গে ফুর্তি করে কাটিয়ে দিতেন।
বসন্ত-প্রান্তে বহিরিনু ঘর হতে
ভিক্ষার লাগি চলেছি ভাণ্ড ধরে–
হেরি মাঠ-ভরা নাচে ফুলদল
নাচে পথ-ঘাট ভরে।
দাঁড়াইনু আমি এক লহমার তরে
কথা কিছু ক’ব বলে
ও মা, এ কি দেখি! সমস্ত দিন
কি করে যে গেছে চলে!
এই আপন-ভোলা লোকটির সঙ্গে যখন আর আর সংসার-বিমুখ শ্ৰমণদের তুলনা করা যায় তখনই ধরা পড়ে শ্রমণ-নিন্দিত প্রকৃতির সঙ্গে এঁর কবিজনীসুলভ গভীর আত্মীয়তা-বোধ। এই সৰ্বং শূন্যং সৰ্বং ক্ষণিকং জগতের প্রবহমাণ ঘটনাবলীকে তিনি আর পাঁচ জন শ্রমণের মত বৈরাগ্য ও বিরক্তির সঙ্গে অবহেলা করছেন না, আবার সৌন্দর্যবিলাসী কবিদের মত চাঁদের আলো আর মেঘের মায়াকেও আঁকড়ে ধরতে অযথা শোকাতুর হচ্ছেন না। বেদনা-বোধ যে রিয়োকোয়ানের ছিল না তা নয়।–তীর কবিতার প্রতি ছত্রে ধরা পড়ে তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয় কত অল্পতেই সাড়া দিচ্ছে—কিন্তু সমস্ত কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর এমন একটি সংহত ধ্যানদৃষ্টি দেখতে পাই যার মূল নিশ্চয়ই বৌদ্ধ-ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের অস্তস্থল থেকে আপন প্রাণশক্তি সঞ্চয় করছে।
অথচ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলে গিয়েছেন, তিনি কখন কাউকে আপনি ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করেন নি, অন্যান্য শ্রমণের মত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন নি।
তাই এই লোকটিকে বুঝতে জাপানেরও সময় লেগেছে। ফিশার বলেন, ১৯১৮ সনে শ্ৰীযুক্ত সোমা গায়েফু কর্তৃক তাইণ্ড রিয়োকোয়ান’ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্ৰ জাপানে এই শ্রমণের নাম ছড়িয়ে পড়ে।
আজ তাঁর খ্যাতি শুধু আপন প্রদেশে, আপন প্ৰব্ৰজ্যাভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়। জাপানের সর্বত্রই তার জীবন, ধর্মমত, কাব্য এবং চিন্তাধারা জানিবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।
সেই উত্তেজনা, সেই আগ্রহ বিদেশী শিক্ষক গায়ক ফিশারকেও স্পর্শ করেছে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর একাগ্ৰ তপস্যার ফলে তিনি যে গ্ৰন্থ প্রকাশ করেছেন তার কল্যাণে আমরাও রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উপরে উল্লিখিত রিয়োকোয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত সোমা গায়েফু ফিশারের গ্ৰন্থকে সপ্ৰেম আশীর্বাদ করেছেন, এবং এ-কথাও বলেছেন যে ফিশারই একমাত্র ইউরোপীয় যিনি শ্রমণ রিয়োকোয়ানের মৰ্মস্থলে পৌঁছাতে পেরেছেন।
জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপরের এক গ্রামে ১৭৫৮ সালে রিয়োকোয়ানের জন্ম হয়। রিয়োকায়ান-বংশ সে অঞ্চলে আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির জন্য সুপরিচিত ছিল। রিয়োকোয়ানের পিতা গ্রামের প্রধান বা অগ্রণীরূপে প্রচুর সম্মান পেতেন।
রিয়োকোয়ানকে বুঝতে হলে তাঁর পিতার জীবনের কিছুটা জানতে হয়। তিনিও কবি ছিলেন এবং তার কবিতাতেও এমন একটি দ্বন্দ্ব সব সময়ই প্ৰকাশ পায় যে দ্বন্দ্বের অবসান কোন কবিই এ জীবনে পান নি। সাধারণ কবি এ-রকম অবস্থায় কাব্য-জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক করে নিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে যতদূর সম্ভব মিলে-মিশে চলার চেষ্টা করেন, কিন্তু রিয়োকোয়ানের পিতার দ্বন্দ্বমুক্তি প্ৰয়াস এতই নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ আস্তরিকতায় উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত কোনো সমাধান না পেয়ে আত্মহত্যা করেন।
রিয়োকোয়ানের অন্যান্য ভাই-বোনেরাও কবিতা রচনা করে জাপানে খ্যাতিলাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনও সমাজের আর পাঁচজনের জীবনের মত গতানুগতিক ধারায় চলতে পারে নি। রিয়োকোয়ানের ছোট দুই ভাই ও এক বোন প্ৰব্ৰজ্যা গ্ৰহণ করেন।
ধন-সম্পত্তি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সব কিছুই ছিল, রাজধানীতে রিয়োকোয়ানের পিতা সুপরিচিত ছিলেন, বসত-গ্রামের অধিবাসীরা রিয়োকোয়ান-পরিবারকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত, তৎসত্ত্বেও কেন পরিবারের পিতা আত্মহত্যা করলেন, তিন পুত্র এক কন্যা চীরবস্ত্ৰ গ্ৰহণ করলেন-এ রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা রিয়োকোয়ান-জীবনীকার অধ্যাপক য়াকব ফিশার করেন নি। তবে কি জাপানের রাজনৈতিক ও সমাজিক জীবন সে-যুগে এমন কোন পক্ষের বিরুদ্ধে হয়ে উঠেছিল যে স্পর্শকাতর পরিবার মাত্রকেই হয় মৃত্যু অথবা প্ৰব্ৰজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে সর্ব সমস্যার সমাধান করতে হত? ফিশার সে-রকম কোন ইঙ্গিতও করেন নি।
ফিশার বলেন, ‘রিয়োকোয়ান শিশু বয়স থেকেই অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির পরিচয় দেন। আর সব ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধূলায় মত্ত থাকত তখন বালক রিয়োকোয়ান তন্ময় হয়ে কন-পুৎসিয়ের তত্ত্ব-গভীর রচনায় প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতেন। তাঁর এই আচরণে যে তার পিতা-মাতা ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত ফিশার দিয়েছেন।
রিয়োকোয়ানের সব জীবনী-লেখকই দুটি কথা বার বার জোর দিয়ে বলেছেন। রিয়োকোয়ান বালক বয়সেও কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি এবং যে যা বলত তিনি সরল চিত্তে তাই বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে ফিশার রিয়োকোয়ানের বাল্যজীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।
রিয়োকোয়ানের বয়স যখন আট বৎসর তখন তার পিতা তারই সামনে একটি দাসীকে অত্যন্ত কঠিন বাক্য বলেন। দাসীর দুঃখে রিয়োকোয়ান বড়ই ব্যথিত হন ও ক্রুদ্ধনয়নে পিতার দিকে তাকান। পিতা তার আচরণ লক্ষ্য করে বললেন, ‘এ রকম চোখ করে বাপ-মায়ের দিকে তাকালে তুমি আর মানুষ থাকবে না, ঐ চোখ নিয়ে মাছ হয়ে যাবে।’ তাই শুনে বালক রিয়োকোয়ান বাড়ি ছেড়ে অন্তর্ধান করলেন। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা চতুর্দিকে সংবাদ পাঠালেন। অবশেষে এক জেলে খবর পাঠাল, সে রিয়োকোয়ানকে সমুদ্রপারের পাষাণন্তুপের কাছে দেখতে পেয়েছে। পিতা-মাতা ছুটে গিয়ে দেখেন, তিনি পাষাণাস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর সমুদ্রের ঢেউ তার গায়ে এসে লাগছে। কোলে করে বাড়ি এনে বাপ-মা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি ওখানে নির্জনে সমস্ত দিন কি করছিলে?’ রিয়োকোয়ান বড় বড় চোখ মেলে বললেন, ‘তবে কি আমি এখনো মাছ হয়ে যাই নি, আমি না দুষ্ট্র ছেলের মত তোমাদের অবাধ্য হয়েছিলুম?’
রিয়োকোয়ান কেন যে সমস্ত দিন সমুদ্রপারে জলের কাছে কাটিয়েছিলেন তখন বোঝা গেল। মাছই যখন হয়ে যাবেন তখন জলের কাছে গিয়ে তার জন্য প্ৰস্তুত হয়ে থাকাই তো প্রশস্ততম পন্থা।
সংসার ত্যাগ করেও রিয়োকোয়ান পিতা-মাতা সম্বন্ধে কখনো উদাসীন হতে পারেন। নি। মায়ের স্মরণে বৃদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ান যে কবিতাটি রচনা করেন সেটি মায়েরই ভালোবাসার মত এমনি সরল সহজ যে অনুবাদে তার সব মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় :–
সকাল বেলায় কখনো গভীর রাতে
আঁখি মোর ধায় দূর সাদৌ(৩) দ্বীপ পানে
শান্ত-মধুর কত না স্নেহের বাণী
মা আমার যেন পাঠায় আমার কানে।
——-
(১) শেলির ‘What if my leaves are falling’ ভিন্ন অনুভূতিতে, ঈষৎ দম্ভপ্রসূত।
(২) Calligrapher = সুদৰ্শন লিপিকর।
(৩) রিয়োকোয়ানের মাতা ‘সাদো’ দ্বীপে জন্মেছিলেন।
স্বয়ংবর চক্র
ট্রামে বাসে মেয়েদের জন্য আসন ত্যাগ করা ভদ্রতা অথবা অপ্রয়োজনীয়, এ সম্বন্ধে সর্বত্র আলোচনা শোনা যায় এবং আলোচনা অনেক সময় অত্যধিক উষ্মাবশত মনকষাকষি সৃষ্টি করে। একদল বলেন, মা-জননীরা দুর্বল, তাহাদিগকে স্থান ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য; অন্য দল বলেন, মা-জননীরা যখন নিতান্তই বাহির হইয়াছেন, তখন বাহিরের কষ্টটা যত শীঘ্ৰ সহ্য করিতে শেখেন ততই মঙ্গল।
মেয়েরা যদি শব্দার্থেই ট্রামে-বাসে বাহির হইতেন, তাহা হইলে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু তাহারা যে শীঘ্রই ব্যাপকর্থে অর্থাৎ নানা প্রকার চাকরি ব্যবসায় ছড়াইয়া পড়িবেন সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ অন্যান্য দেশে যাহা পাঁচিশ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। এদেশে তাহার পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে। সব কিছু ঘটিবে, এমন কথাও বলিতেছি না।
১৯১৪-এর পূর্বে জর্মন পরিবারকর্তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেন, পুত্রকে শিক্ষাদানের গ্যারান্টি দিতে আমি প্রস্তুত, কন্যাকে বর দানের। দেশের অবস্থা সচ্ছল ছিল; যুবকেরা অনায়াসে অর্থোপার্জন করিতে পারিত বলিয়াই যৌবনেই কিশোরীকে বিবাহ কইরায় সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিবার পূর্বেই কিশোরীদের বিবাহ হইয়া যাইত, তাহারা বড় জোর আবিটুর বা ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়িবার সুযোগ পাইত।
১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধে, দেশের প্রায় সকল যুবককেই রণাঙ্গনে প্রবেশ করিতে হইল। মেয়েদের উপর ভার পড়িল খেতি-খামার করিবার, কারখানা দোকান আপিস চালাইবার, ইস্কুলে পড়াইবার, ট্রাম ট্রেন চালু রাখিবার। জর্মনীর মত প্রগতিশীল দেশেও মেয়েরা স্বেচ্ছায় হেঁসেল ছাড়ে নাই, নাচিতে-কুঁদিতে বাহির হয় নাই। সামরিক ও অর্থনৈতিক বন্যা তাহাদের গৃহবহ্নি নির্বাপিত করিয়াছিল, হোটেলের আগুন শতগুণ আভায় জুলিয়া উঠিয়াছিল।
যুদ্ধের পর যুবকেরা ফিরিয়া দেখে, মেয়েরা তাহাদের আসনে বসিয়া আছে। বেশির ভাগ মেয়েরা আসন ত্যাগ করিতে প্ৰস্তুত ছিল, যদি উপাৰ্জনক্ষম বর পাইয়া ঘরসংসার পাতিবার ভরসা তাহাদিগকে কেউ দিতে পারিত। কিন্তু সে ভরসা কোথায়? জর্মনীতে তখন পুরুষের অভাব। তদুপরি ইংরাজ ফরাসি স্থির করিয়াছে জর্মনীকে কাঁচা মাল দেওয়া বন্ধ করিয়া তাহার কারবার রুদ্ধশ্বাস করিবে; জর্মনীর পুঁজির অভাব ছিল তো বটেই।
তখন এক অদ্ভূত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হইল। মেয়েরা চাকরি ছাড়ে না, বর পাইবার আশা দুরাশা বলিয়া চাকরি ছাড়িলে খাইবে কি, পিতা হৃতসর্বস্ব ভ্ৰাতা যুদ্ধে নিহত অথবা বেকার। বহু যুবক বেকার, কারণ মেয়েরা তাঁহাদের আসন গ্ৰহণ করিয়া তাঁহাদের উপার্জনক্ষমতা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিবাহ করিতে অক্ষম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে সমস্যাটি জটিল নয়। যুবকেরা পত্নীর উপার্জনে সন্তুষ্ট হইলেই তো পারে। কিন্তু সেখানে পুরুষের দম্ভ যুবকের আত্মসম্মানকে আঘাত করে। পত্নীর উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষ জীবনযাপন করাকে কাপুরুষতা মনে করে। মেনীমুখো, ঘরজামাই হইতে সহজে কেহ রাজী হয় না; বিদেশে না, এদেশেও না। ইংলন্ডে তো আরো বিপদ। বিবাহ করা মাত্র যুবতীকে পদত্যাগ করিতে হইত-স্বামী উপার্জনক্ষম হউন আর নাই হউন (রেমার্কের ‘ডের বেকৎস্যুক’—দ্রষ্টব্য)।
যত দিন যাইতে লাগিল গৃহকর্তারা ততই দেখিতে পাইলেন যে, মেয়েকে বর দিব,–ভালোই হউক আর মন্দই হউক-এ গ্যারান্টি আর জোর করিয়া দেওয়া যায় না। কাজেই প্রশ্ন উঠিল, পিতার মৃত্যুর পর কন্যা করিবে কি? সে তো ম্যাট্রিক পাস করিয়া বাড়িতে বসিয়া অলস মস্তিষ্ককে শয়তানের কারখানা করিয়া বসিল। এদিকে ওদিকে তাকাইতেও আরম্ভ করিয়াছে। না হয় তাহাকে কলেজেই পাঠাও; একটা কিছু লইয়া থাকিবে ও শেষ পর্যন্ত যদি সেখানে কোনো ছোকরাকে পাকড়াও না করিতে পারে। তবু তো লেখাপড়া শিখিবে, তাহারি জোরে চাকরি জুটাইয়া লইবে।
আমি জোর করিয়া বলিতে পারি ১৯২৪-৩২-তে যে সব মেয়েরা কলেজে যাইত তাহাদের অল্পসংখ্যকই উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী হইয়া, কারণ বারে বারে দেখিয়াছি ইহারা উপাৰ্জনক্ষম বর পাওয়া মাত্রই ‘উচ্চশিক্ষাকে’ ভালো করিয়া নমস্কার না করিয়াই অর্থাৎ কলেজ-আপিসে রক্ষিত সার্টিফিকেট মেডেল না লইয়াই-জুটিত গির্জার দিকে। আরেকটি বস্তু লক্ষ্য করিবার মত ছিল–তাহা সভয় নিবেদন করিতেছি। ইহাদের অধিকাংশই দেখিতে উর্বশী মেনকার ন্যায় ছিলেন না। সুন্দরীদের বিবাহ ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইত–তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসিবে কোন দুঃখে? কলেজে যে কয়টি সুন্দরী দেখা যাইত, তাহাদের অধিকাংশ অধ্যাপক-কন্যা।
অচ্ছেদ্য চক্ৰ ঘুরিতে লাগিল আরও দ্রুত বেগে। কলেজের পাস করা মেয়ে আস্কারা পাইয়াছে বেশি। যে চাকুরিবাজারে সাধারণ মেয়ে প্রবেশ করিতে ভয় পাইত তাহারা সেই সব চাকুরির বাজারও ছাইয়া ফেলিল-—চক্রের গতি দ্রুততর হইল। পার্থের সন্ধান নাই–তিনি তখনো অজ্ঞাতবাসে–স্বয়ংবির চক্র ছিন্ন করিবে কে?
কিন্তু ইতোমধ্যে সেই নিয়ত ঘূর্ণ্যমান স্বয়ম্বর চক্রের একটি স্ফুলিঙ্গ নৈতিক জগতে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।
মেয়েরা অর্থে পার্জন করিতেছে। পিতা মৃত। পরিবার পোষণ করিতে হয় না। বিবাহের আশা নাই। অর্থ সঞ্চয় করিবে কাহার জন্য? নিরানন্দ, উত্তেজনাহীন শুষ্ক জীবন কেনই বা সে যাপন করিতে যাইবে? অভিভাবকহীন যুবতী ও প্রৌঢ়ারা তখন বিলাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দোষ দিয়া কি হইবে? পিতা বা ভ্রাতা না থাকিলে অরক্ষণীয়ার কি অবস্থা হয় তাহা বেদেই বর্ণিত হইয়াছে—যতদূর মনে পড়িতেছে কোন এক বরুণ মন্ত্রেই-ঋষি সেখানে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন।
উপার্জনক্ষম যুবতীরা বিলাসের প্রশ্ৰয় দেওয়া মাত্ৰই চক্র দ্রুততর হইল। যে সব যুবকেরা অন্যথা বিবাহ করিত, তাহারা এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্ৰহণ করিল। মুক্ত হট্টে দুগ্ধ যখন অপর্যাপ্ত তখন বহু যুবক গাভী ক্রয় করা অবিমূষ্যকারিতার লক্ষণ বলিয়া স্থির করিল। বিবাহ-সংখ্যা আরো কমিয়া গেল—গির্জার বিবাহ পুরোহিতদের দীর্ঘতর অবকাশ মিলিল। নাইট ক্লাবের সৃষ্টি তখনই ব্যাপকভাবে হইল, ‘গণিকা’ জাতির জন্ম। হইল—ইহাদের নাম ইউরোপীয় সর্বভাষায় জিগোলো। যে পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনে জীবন ধারণ করিতে ঘৃণা বোধ করিত, সে-ই গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইল (মাউরার জর্মনী ‘পুটস দি ক্লক ব্যাক’ দ্রষ্টব্য)।
তখন পুরুষ বলিল, ‘স্ত্রীপুরুষে যখন আর কোনো পার্থক্যই রহিল না, তখন পুরুষ ট্রামে-বাসে স্ত্রীলোকদিগের জন্য আসন ত্যাগ করিবে কেন?’ উঠিয়া দাঁড়াইলেও তখন বহু মেয়ে পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইত না। সব কিছু তখন ৫০/৫০। আমার দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস কলিকাতা কখনও ১৯৩২-এর বার্লিনের আচরণ গ্ৰহণ করিবে না। বাঙালি দুর্ভিক্ষের সময় না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে; কুকুর বিড়াল খায় নাই। তবুও সমাজপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম–অর্থনৈতিক কারণে মানুষ কি করিয়া নৈতিক জগতে ধাপের পর ধাপ নামিতে বাধ্য হয়।
অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন করিবেন, জর্মনীর স্বয়ংবর চক্ৰ কি কেহই ছিন্ন করিতে সক্ষম হন নাই? হইয়াছিলেন। সে বীর হিটলার। পার্থের ন্যায় তাহারও নানা দোষ ছিল, কিন্তু অজ্ঞাতবাসের পর তিনিই চক্ৰভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে ড্রেসডেন শহরে এক নির্দিষ্ট দিনে চারিশত যুবক-যুবতীকে সগর্বে শোভাযাত্ৰা করিয়া দল বঁধিয়া বিবাহ করিতে যাইতে দেখিলাম। অন্য শহরগুলিও পশ্চাৎপদ রহিল না; সর্বত্র সপ্তপদী সচল হইয়া উঠিল। ১৯৩৮ সালে গিয়া দেখি কলেজগুলি বৌদ্ধ মঠের ন্যায় নারীবর্জিত। হিটলার কি কৌশলে চক্ৰভেদ করিয়াছিলেন সে কথা আরেক দিন হইবে!
হিন্দু-মুসলমান-কোড বিল
শাস্ত্ৰে সব পাওয়া যায়—কোনো কিছুর অনটন নেই। সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে চান, না বিলিয়ে দিতে চান; পুজো করতে চান, না করতে চান—একখানা কিংবা বিশখানা; পুজোপাজ করতে চান কিংবা ব্যোম ভোলানাথ বলে বুদ হয়ে থাকতে চান, এমন কি মরার পর পরশুরামী স্বর্গে গিয়ে অন্সরাদের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে চান কিংবা রবি ঠাকুরী ‘কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই হয়ে গিয়ে নিগুণ নির্বাণানন্দ লাভ করতে চান, তাবৎ মালই পাবেন।
তা না হলে সতীদাহ বন্ধ করার সময় উভয় পক্ষই শাস্ত্ৰ কপচালেন কেন? বিধবাবিবাহ আইন পাস করার সময়, শারদা বিলের হাঙ্গামহুজ্জুতের সময় উভয় পক্ষই তো শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছিলেন, এ-কথা তো আর কেউ ভুলে যায় নি।
শুধু হিন্দুশাস্ত্র না, ইহুদি খ্ৰীষ্টান মুসলিম সব শাস্ত্রেরই ঐ গতি। শুধু হিন্দুশাস্ত্র এঁদের তুলনায় অনেক বেশি বনেদী বলে এর বাড়িতে দালান-কোঠার গোলকধাঁধা ওঁদের তুলনায় অনেক বেশি, পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা পদে পদে। তাতে অবশ্য বিচলিত হওয়ার মত কিছুই নেই, কারণ স্বয়ং ষীশুখ্ৰীষ্ট নাকি বলেছেন, যে হোভার আপনি বাড়িতে দালান-কোঠা বিস্তর।
তাই শাস্ত্রের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তাতে ফয়দাও এস্তার। মুসলিম শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ চর্চা করেছি বলেই মোল্লা-মৌলবীকে আমি বড় বেশি ডরাই নে। কুড়েমি করে জুম্মার নামাজে যাই নি, মোল্লাজী রাগত হয়ে প্রশ্ন শুধালেন, যাই নি কেন? চট করে শাস্ত্ৰবচন উদ্ধৃত করলুম, আমি যে জায়গায় আছি সেটাকে ঠিক শহর (মিসর) বলা চলে না। অতএব জুম্মার নামাজ অসিদ্ধ। ব্যস, হয়ে গেল। ঠিক তেমনি বিয়ে যখন করতে চাই নি, তখন আমি শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছি আবার ওজীর সাহেব ফজলু ভায়া যখন পরিপক্ক বৃদ্ধ বয়সে তরুণী গ্ৰহণ করলেন, তখন তিনিও হাদীস (স্মৃতি) কপচালেন।
গ্রামাঞ্চলে থাকতে হলে কুইনিনের মতো শাস্ত্ৰ নিত্য সেব্য।
সে কথা থাক।
হিন্দু-রমণী তালাক (লগ্নচ্ছেদ) দিয়ে নবীন পতি বরণ করতে পারবেন কি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে। আমার শিরঃপীড়া, আমার গৃহিণী বেঁকে গিয়ে কিছু একটা করে ফেলবেন না তো! এ প্রশ্ন মনে উঠত না, কিন্তু হিন্দু কোড বিল আসর গরম করে তোলাতে মুসলমান ভায়াদের টনক নড়েছে। খুলে কই।
হঠাৎ এক গুণী খবরের কাগজে পত্ৰাঘাত করলেন,-তিনি হিন্দু না মুসলমান মনে নেই-হিন্দু রমণী যদি লগ্নচ্ছেদ করবার অধিকার পায়, তবে মুসলমান রমণীতেও সে অধিকার বর্তবে না কেন? ঠিকই তো। কিন্তু উত্তরে আর পাঁচজন মুসলমান বললেন,–কেউ খেঁকিয়ে, কেউ মুরুব্বীর চালে, কেউ বা হিন্দু ভায়াদের পিঠে আদরের থাবড়া দিয়েমুসলমান শাস্ত্ৰ নূতন কোড দিয়ে রদ-বদল করার কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলমান রমণীর যে অধিকার আছে তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট-ওসব মালের প্রয়োজন হিন্দুদের।
লক্ষ্য করলুম, কোনো মুসলমান রমণী খবরের কাগজে এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।
তাই প্রশ্ন, লগ্নচ্ছেদ করার জন্য মুসলমান পুরুষ রমণীর কতটুকু অধিকার? এ আলোচনায় মুসলমানদের কিছুটা লাভ হবে, হিন্দুদের কোনো ক্ষতি হবে না।
মৌলা বখশ মিঞা যে-কোনো মুহূর্তে বেগম মৌলাকে তিনবার ‘তালাক, তালাক, তালাক’ বললেই তালাক হয়ে গোল—স্বয়ং শিবেরও সাধ্য নেই তিনি তখন সে তালাক ঠেকান, এস্থলে ‘শিব’ বলতে অবশ্য মোল্লা-মৌলাবী বোঝায়।
বেগম মৌলা সতীসাধ্বী। আজীবন স্বামীর সেবা করেছেন। তার তিনটি পুত্রকন্যা, সবচেয়ে ছোটটির বয়স দশ কিংবা বারো। তার বাপের বাড়িতে কেউ নেই। তিনি বিগত যৌবনা–বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তিনি পুনরায় বিয়ে করতে চাইলেও নূতন বর পাবেন না।
বেগম মৌলাকে তদণ্ডেই পতিগৃহ ত্যাগ করতে হবে। কাচ্চাব্বাচ্চাদের উপরও তাঁর কোনো অধিকার নেই–নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য হলে অবশ্য আলাদা কথা।
‘তালাক, তালাক, তালাক’ বলার জন্য মৌলা সাহেবকে কোনো কারণ দর্শাতে হবে না, কেন তিনি গৃহিণীকে বর্জন করছেন; তার কোন অপরাধ আছে কি না, তিনি অসতী কিংবা চিরক্কাগ্রা, কিংবা বদ্ধ উন্মাদ-এর কোনো কারণই দেখাবার জন্য কেউ তাকে বাধ্য করতে পারে না। এস্থলে নিরঙ্কুশ, চৌকাশ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’।
(জানি, মৌলা সাহেব হেড আপিসের বড়বাবুর মতো বড় শান্ত স্বভাব ধরেন। হঠাৎ তিনি ক্ষেপে গিয়ে এরকম ধারা কিছু একটা করবেন না, কিন্তু সেকথা অবান্তর। এখানে প্রশ্ন, মৌলার হক কতটুকু, বেগম মৌলারই বা কতটুকু? তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ভদ্র হিন্দু সচরাচর বিনা কুসুরে একমাত্র পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু কস্মিনকালেও করেন না একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়।)
যাঁরা তালাক আইনের কোনো পরিবর্তন চান না তারা উত্তরে বলবেন, আরো বাপু, তালাক দেওয়া কি এতই সোজা কর্ম? ‘মহরে’র কথাটি কি বেবাক ভুলে গেলে? মৌলার মাইনে তিন শ টাকা। ‘মহরের টাকা পাঁচ হাজার। অত টকা পাবে কোথায় মৌলা সাহেব?
হিন্দু পাঠককে এই বেলা ‘মহর’ জিনিসটি কি সেটি বুঝিয়ে বলতে হয়। ‘মহর’ অর্থ মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে স্ত্রীধন। বিয়ের সময় মৌলাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, তার বেগমকে তিনি কতটা স্ত্রীধন দেবেন। মৌলা বলেছিলেন, পাঁচ হাজার (অবস্থাভেদে পঞ্চাশ একশ, এক হাজার বা পাঁচ লক্ষ্যও হতে পারে) এবং এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন, বেগম সাহেবা যে-কোনো মুহূর্তেও স্ত্রীধন তলব করলে তিনি তদ্দণ্ডেই নগদা-নগদি আড়াই হাজার ঢেলে দেবেন এবং বাকী আড়াই হাজার কিস্তিবন্দিতে শোধ দেবেন।
এসব শুধু মুখের কথা নয়। এ সমস্ত জিনিস বিয়ের রাতে দলিল লিখে তৈরি করা হয় ও পরে ‘মেরেজ রেজিস্ট্রারে’র আপিসে পাকাপোক্ত রেজিস্ট্রি করা হয়। মৌলা এ টাকাটা ফাঁকি দিতে পারবেন না, সে কথা সুনিশ্চিত।
উত্তরে নিবেদন :
মৌলার গাঁঠে পাঁচ হাজার টাকা থাক। আর নাই থাক, তিনি যে স্ত্রীকে তালাক দিলেন, সেটা কিন্তু অসিদ্ধ নয়। টাকা না দিতে পারার জন্য শেষ তক মৌলার সিভিল জেল হতে পারে, কিন্তু তালাক তালাকই থেকে গেল। অর্থাৎ একথা কেউ মৌলাকে বলতে পারবে না, তোমার যখন পাঁচ হাজার টাকা রেস্ত নেই, তাই তালাক বাতিল, বেগম মৌলা তোমার স্ত্রী এবং স্ত্রীর অধিকার তিনি উপভোগ করবেন।
মোদ্দা কথা, তালাক হয়ে গেল, টাকা থাক। আর নাই থাক।
***
পুনরায় নিবেদন করি, শাস্ত্ৰ কি বলেন সে-কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। কুরানশরীফ যা বলেছেন, তার যেসব টীকা-টিপ্পানী লেখা হয়েছে, তার উপর যে বিরাট শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে দেশাচার-লোকচার মিলে গিয়ে উপস্থিত যে পরিস্থিতি বিদ্যমান। তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা। সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে একে অন্যের উপর কতখানি অধিকার, বিশেষ করে একে অন্যকে বর্জন করার অধিকার করার কতটুকু সেই নিয়ে আলোচনা ।
পূর্বেই নিবেদন করেছি। স্বামী যে কোনো মুহূর্তে স্ত্রীকে বর্জন করতে পারেন। তাকে তখন কোনো কারণ কিংবা অজুহাত দর্শাতে হয় না। তবে তিনি যে ‘মহর’ বা স্ত্রীধন দেবেন বলে প্ৰতিজ্ঞা করেছিলেন সে অর্থ তাকে দিতে হবে। অবশ্য না দিতে পারলে যে তালাক মকুব হবে তাও নয়। স্ত্রী তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীর মাইনে ‘অ্যাটাচ’ করতে পারেন, আদালতের ডিগ্রি নিয়ে সম্পত্তি ক্ৰোক করতে পারেন; এক কথায় উত্তমণ অধমৰ্ণকে যতখানি নাস্তানাবুদ করতে পারেন ততখানি তিনিও করতে পারেন।
উত্তম প্রস্তাব। এখন প্রশ্ন স্ত্রী যদি স্বামীকে বর্জন করতে চান তবে তিনি পারেন কি না? যদি মনে করুন, স্ত্রী বলেন, ‘এই রইল তোমার স্ত্রী-ধন, আমাকে খালাস দাও’। কিম্বা যদি বলেন, ‘তুমি আমাকে যে স্ত্রীধন দেবে বলেছিলে সে স্ত্রীধনে আমার প্রয়োজন নেই, আমি তোমাকে বর্জন করতে চাই, তবু স্বামী সাফ না’ বলতে পারেন। অবশ্য স্ত্রী স্বামীকে জ্বালাতন করার জন্য তার স্ত্রীধন তদণ্ডেই চাইতে পারেন-করণ শ্ৰীধন তলব করার হক স্ত্রীর সব সময়ই আছে, স্বামী তালাক দিতে চাওয়া না-চাওয়ার উপর সেটা নির্ভর করে না। স্বামী যদি সে ধন দিতে অক্ষম হন তা হলেও স্ত্রী তালাক পেলেন না। অর্থাৎ তিনি যদি পতিগৃহ ত্যাগ করে ভিন্ন বিবাহ করতে চান তবে সে বিবাহ অসিদ্ধ; শুধু তাই নয়, পুলিশ স্ত্রী এবং নবীন স্বামী দুজনের বিরুদ্ধে বিগেমি’র মোকদ্দমা করতে পারবে।
পক্ষান্তরে আবার কোনো স্ত্রী যদি স্ত্রীধনটি ভ্যানিটি-ব্যাগস্থ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকেন তবে স্বামীও তাকে জোর করে আপনি বাড়িতে নিয়ে আসতে পারেন না। আইন স্বামীকে সে অধিকার দেয়, কিন্তু আনবার জন্য পুলিশের সাহায্য দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। আপনি যদি জোর করে আনতে যান। তবে শালী-শালাজের হস্তে উত্তমমাধ্যমের সমূহ সম্ভাবনা ।
তখন আপনি আর কি করতে পারেন? তাকে তালাক দিয়ে হৃদয় থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে পারেন। আর আপনি যদি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হন তবে আপনি তালাক না দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন। তাতে করে আর কিছু না হোক স্ত্রী অন্তত আরেকটা লোককে বিয়ে করতে পারবেন না।
খুব বেশি না হলেও কোনো কোনো সময় এরকম হয়ে থাকে। পরিস্থিতিটা দু রকমের হয় ।
হয় স্বামী বদরাগী, কিংবা দুশ্চরিত্র। স্ত্রীকে খেতে পরতে দেয় না, মারধোর করে। সহ্য না করতে পেরে স্ত্রী বাপ কিংবা ভাইয়ের বাড়িতে পালাল (বাপ বেঁচে না থাকলে ভাইও আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়, কারণ ভাই যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে তাতে বোনেরও অংশ আছে)। সেখান থেকে সে স্ত্রধনের তলব করে মোকদ্দমা লাগাল। স্বামীর কণ্ঠশ্বাস–অত টাকা যোগাড় করবে। কোথা থেকে?
তখন সাধারণত মুরুব্বীরা মধ্যিখানে পড়েন-বিশেষত সেই মুরুঝবীরা যাঁরা বিয়েটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁরা পতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, ‘তোমাতে ওতে যখন মনের মিল হয় নি তখন কেন বাপু মেয়েটাকে ভোগাচ্ছি। তালাক দিয়ে ওকে নিষ্কৃতি দাও, বেচারী অন্য কোথাও বিয়ে করুক।’
বেয়াড়া বদমায়েশ স্বামী হলে বলে, ‘না, মরুকগে বেটি। আমি ওকে তালাক দেব না।’
মুরুব্বীরা বলেন, ‘তবে ঢালো ‘‘মহরে’’র ঢাকা! না হলে বসতবাড়ি বিক্রি হবে, কিংবা মাইনে অ্যাটাচুড হবে। তখন বুঝবে ঠ্যালাটা।’
বিশ্বাস করবেন না, এরকম দুশমন ধরনের স্বামীও আছে যে বাড়ি বিক্রয় করে মহারের শেষ কপর্দক দেয়। কিন্তু তালাক দিতে রাজী হয় না।
কিংবা সে শেষ পর্যন্ত রাজী হয় যে বিবি তার স্ত্রীধন তলব করবেন না। আর সেও তাকে তালাক দিয়ে দেবে।
কিন্তু এটা হল আপোসে ফৈসালা। আইনের হক স্ত্রীলোকের নেই যে সে পতিকে বর্জন করতে পারে। তবু এস্থলে পুনরায় বলে রাখা ভালো, ‘মহরে’র টাকা দেবারু ভয়ে অনেক স্বামী স্ত্রীর উপর চোট-পাট করা থেকে নিরস্ত থাকেন।
এখন প্রশ্ন, স্বামীর যদি গলিত কুণ্ঠ হয়, কিংবা সে যদি বদ্ধ উন্মাদ বর্তীয়, যদি তার যাবজীবন কারাদণ্ড হয়, যদি সে বার বার কুৎসিতরোগ আহরণ করে স্ত্রীকে সংক্রামিত করে, যদি সে লম্পট বেশ্যাসক্ত হয় তবে কি স্ত্রী তাকে আইনত তালাক দিতে পারেন না?
শুনেছি, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে ‘তুমি আমার মায়ের মতো’ অর্থাৎ এই উক্তি দ্বারা সে প্ৰতিজ্ঞা করে যে স্ত্রীকে সে তার ন্যায্য যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। তবে নাকি সে স্ত্রী মোকদ্দমা করে আদালতের পক্ষ থেকে তালাক পেতে পারে।