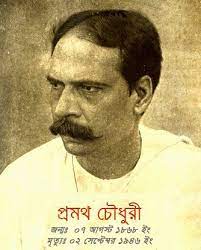- বইয়ের নামঃ সাহিত্য
- লেখকের নামঃ প্রমথ চৌধুরী
- বিভাগসমূহঃ প্রবন্ধ
অভিভাষণ
উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত আজ বাইশ বৎসর পূর্বে এই রাজশাহি শহরে আমি সর্বজনসমক্ষে সসংকোচে দুটি-চারিটি কথা বলি। আমার জীবনে সেই সর্বপ্রথম বক্তৃতা। কোনো দূরভবিষ্যতে আমি যে এই সভার মুখপাত্রস্বরূপে আবার আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব, সেদিন এ কথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।
আজিকার ব্যাপারে যাঁহারা কর্মকর্তা সেদিনও তাহারাই কর্মকর্তা ছিলেন। মহারাজ নাটোর এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উদ্যোগেই সে সভা আহূত হয়। এবং তাঁহাদের অনুরোধেই আমি সে সভার প্রধান বক্তা শ্ৰীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদানুসরণ করি। এ সভারও পতির আসন রবীন্দ্রনাথের জন্যই রচিত হইয়াছিল; তাঁহার অনুপস্থিতিতে পূর্বোক্ত বন্ধুদ্বয়ের অনুরোধে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়মত আমি তাঁহার ত্যক্ত এই রিক্ত আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাঁহারা আমাকে প্রথমে আসরে নামান, তাঁহারাই আজ আমাকে এ অসিরের প্রধান নায়ক সাজাইয়া খাড়া করিয়াছেন। এ পদ অধিকার করিবার আমার কোনোরূপ যোগ্যতা আছে কি না, সে বিচার তাঁহারও করেন নাই, আমাকেও করিতে দেন নাই।
এ আসন গ্রহণ করিবার অধিকার যে আমার নাই, তাহা আমার নিকট অবিদিত নয়। আমি অবসরমত সাহিত্যচর্চা করি, কিন্তু সে গৃহকোণে এবং নির্জনে। বক্তা ও লেখক একজাতীয় জীব নন; ইহাদের পরস্পরের প্রকৃতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন, তিনি শ্রোতার মন জবরদখল করেন; অপর পক্ষে লেখক পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না; লেখক পাঠকের অবসরের সাথী। অক্ষরের নীরব ভাষায় একটি অদৃশ্য শ্রোতার কানে কানে আমরা নানা ছলে নানা কথা বলিতে পারি; কিন্তু জনসমাজে আমাদের সহজেই বাকরোধ হয়। যে বাণী সবুজ পত্রের আবডালে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তাহা সূর্যের নগ্ন কিরণের স্পর্শে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। অথচ গুণীসমাজে সুপরিচিত হইবার লোভও আমাদের পুরা মাত্রায় আছে। সাহিত্যের রঙ্গভূমিতে দর্শকের নয়ন-মন। আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিত্য লালায়িত, অথচ লেখকের ভাগ্যে পাঠকের সাক্ষাৎকারলাভ কচিৎ ঘটে। প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি এবং নিন্দার শিলাবৃষ্টি উভয়ই আমাদের শিরোধার্য, একমাত্র উপেক্ষাই আমাদের নিকট চির অসহ্য। সুতরাং সাহিত্যসমাজে যথাযোগ্য আসন লাভ করাতেই আমরা কৃতার্থতা লাভ করি। দণ্ডী বলিয়াছেন যে–
কৃশে কবিত্বেহপি জনাঃ কৃতশ্রমা
বিদগ্ধগোষ্ঠীষু বিহর্তুমীশতে।
আমাদের ন্যায় প্রতিভাবঞ্চিত লেখকদিগের সকল শ্রম বিদগ্ধগোষ্ঠীতে স্থানলাভ করাতেই সার্থক হয়।
অতএব অন্য কারণভাবেও অন্ততঃ দু দিনের জন্যও উত্তরবঙ্গের বিদগ্ধগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি হইবার লোভ সম্ভবতঃ আমি সংবরণ করিতে পারিতাম না।
২.
কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার বিশেষ করিয়া একটি নিজস্ব কারণ আছে, যাহার দরুন আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে এ আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। এ স্থলে কোনোরূপ বিনয়ের অভিনয় করা আমার অভিপ্রায় নয়। অযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চপদস্থ করা যে তাহাকে অপদস্থ করিবার অতি সহজ উপায়, এ জ্ঞান আমার আছে। এ সত্ত্বেও আমি যে আপনাদের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি তাঁহার কারণ উত্তরবঙ্গের আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। আমার দেশ বলিতে আমি প্রথমতঃ এই প্রদেশই বুঝি। বারেন্দ্র সমাজের সহিত আমার নাড়ির যোগ আছে, বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার রক্তের টান আছে। উত্তরবঙ্গের প্রতি আমার অনুরাগকে এক হিসাবে মৌলিক বলিলেও অত্যক্তি হয় না; কেননা এই দেশের মাটিতেই এ দেহ গঠিত। আমার বিশ্বাস, বাস্তুভিটার প্রতি মানুষমাত্রেরই যে স্বাভাবিক টান আছে, সেই আদিম মনোভাবের অটল ভিত্তির উপরেই সভ্য মানবের স্বদেশবাৎসল্য প্রতিষ্ঠিত। অতীত-অনাগতের এই মিলনক্ষেত্রেই আমরা আমাদের আত্মার সহিত আমাদের পূর্বপুরুষদিগের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাই। এই বাস্তুপ্রীতিই ক্রমে প্রসারলাভ করিয়া স্বদেশপ্রীতিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে দেশের যে ভূভাগ আমাদের পূর্বপুরুষদিগের স্মৃতির সহিত একান্ত জড়িত, সে প্রদেশের প্রতি অন্তরের টান থাকা মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার পারিবারিক পূর্বকাহিনী এই বরেন্দ্রমণ্ডলের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া আমার জাতীয় পূর্বজন্মের স্মৃতি, আর্যাবর্ত দূরে থাক্, কান্যকুজেও গিয়া পৌঁছায় না। সুতরাং বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার যে প্রগাঢ় অনুরাগ আছে সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এবং সেই মজ্জাগত প্রীতিবশতঃই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যপরিষৎ যে গুরুভার আমার মস্তকে ন্যস্ত করিয়াছেন, আমি তাহা বিনা আপত্তিতে নতশিরে গ্রহণ করিয়াছি।
৩.
এই প্রসঙ্গে আমি এইরূপ প্রাদেশিক সাহিত্যসভার সার্থকতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কাহারও কাহারও মতে এইরূপ পৃথক পৃথক্ পরিষদের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যসমাজেও প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করা হয়। এ অভিযোগের অর্থ আমি অদ্যাবধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশে এই জাতীয় সভাসমিতির সংখ্যা যত বৃদ্ধিলাভ করিবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এবং আমার মতে এইসকল প্রাদেশিক সাহিত্যসমিতির পক্ষে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র রক্ষা করাই শ্রেয়। আমি শিক্ষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের পক্ষপাতী। কোনো-একটি আঢ্যপরিষদের শাসনাধীন থাকিলে প্রাদেশিক পরিষৎগুলি সম্যক্ স্মৃতি লাভ করিতে পারিবে না। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রধান ত্রুটি তাঁহার বৈচিত্র্যের অভাব। বঙ্গদেশের সহিত বঙ্গসাহিত্যের সাক্ষাৎপরিচয় ঘটিলে এ অভাব দূর হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে আমি দক্ষিণবঙ্গের প্রাধান্য অস্বীকার করি না। আমার বিশ্বাস, এ ভাষার গুণে দক্ষিণবঙ্গ চিরকাল সে প্রাধান্য রক্ষা করিবে; সুতরাং উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের সাহিত্যপরিষদের প্রতি কোনোরূপ কটাক্ষপাত করা কলিকাতার পক্ষে সংগতও নহে, শোভনও নহে। বস্তুতঃ সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের উপর নবনাগরিক-সাহিত্যের প্রভাব এত বেশি যে, আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যে প্রাদেশিকতার নামগন্ধও থাকে না। এমনকি, কোনো হতভাগ্য লেখকের রচনা যদি নাগরিক মতে নাগরিকতা দোষে দুষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে সকল প্রদেশেই সে রচনা প্রাদেশিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।
৪.
উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ এই যে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি কর্তৃক আবিষ্কৃত বরেন্দ্রমণ্ডলের পূর্বগৌরবের নিদর্শনসকলের বলে উত্তরবঙ্গের মনে ঈষং অহংজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে। এ কথা সত্য কি না তাহা আমি জানি না। যদিই বা উত্তরবঙ্গ তাঁহার অতীত-গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করে তাহাতেই বা ক্ষতি কি। সমগ্র বঙ্গের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে প্রদেশমাত্রেরই অহংকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।
কেহ কেহ বলেন যে, কোনোরূপ প্রদেশবাৎসল্যের প্রশ্রয় দেওয়া কর্তব্য নহে, কেননা ঐরূপ সংকীর্ণ মনোভাব উদার স্বদেশবাৎসল্যের প্রতিবন্ধক। আমি পুর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারেন যে, ইহারা যে মনোভাবকে সংকীর্ণ বলেন আমি তাহাকেই প্রকৃত উদার মনোভাবের ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞান করি। যে স্থলে কোনো অংশের প্রতি প্রীতি নাই, সে স্থলে সমগ্রের প্রতি ভক্তির মূল কোথায় তাহা আমি খুঁজিয়া পাই না।
অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যে-মনোভাবকে অতি উদার বলা হয় তাঁহার কোনরূপ ভিত্তি নাই। বাংলাদেশের সহিত, বাংলার ইতিহাসের সহিত, বঙ্গসাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় নাই অথচ বঙ্গমাতার নামে মুগ্ধ, এইরূপ লোক আমাদের শিক্ষিত সমাজে বিরল নহে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহাদের প্রতাপ দুর্দান্ত এবং প্রতিপত্তি অসীম। এইরূপ উদার মনোভাবের অবলম্বন কোনো বস্তুবিশেষ নয়, কিন্তু একটি নাম মাত্র। এইরূপ স্বদেশ প্রীতির মূল হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। এইরূপ স্বদেশি মনোভাব বিদেশি পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁথিগত পেটিয়টিজমের সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করা যায় কি যায় না তাহা আমার অবিদিত, কিন্তু সাহিত্য যে সৃষ্টি করা যায় না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নামের মাহাত্ম আমি অস্বীকার করি না। সদলবলে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন করিতে করিতে মানুষে দশাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ ক্ষণিক উত্তেজনার প্রসাদে পৃথিবীর কোনো কার্য সুসিদ্ধ হয় না। সিদ্ধি সাধনার অপেক্ষা রাখে এবং সাধনা স্থিরবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং তথাকথিত সংকীর্ণ প্রদেশবাৎসল্য যদি এই জাতীয় উদার মনোভাবের বিরোধী হয়, তাহা হইলে এইরূপ সংকীর্ণ মনোভাবের চর্চা করা আমি একান্ত শ্রেয় মনে করি। কিন্তু আসলে এসকল অভিযোগের মূলে কোনো সত্য নাই। কেননা একমাত্র সাহিত্যই এ পৃথিবীতে মানবমনের সকল প্রকার সংকীর্ণতার জাতশত্রু। জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালোনা কেন, তাঁহার আলোক চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে; ভাবের ফুল যেখানেই ফুটুক-না কেন, তাঁহার গন্ধ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। মনোজগতে বাতি জ্বালানো এবং ফুল ফোঁটানোই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম এবং একমাত্র কর্ম। কোনো জাতির মনের ঐক্যসাধনের প্রধান উপায় সাহিত্য; কেননা ভাষার ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের মূল। ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র হইতে পারে, কিন্তু বাঙালি যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাঁহার কারণ, এক-ভাষার বন্ধনে এ দেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, ব্রাহ্মণ শূদ্র হিন্দু মুসলমান সকলেই আবদ্ধ। সকল প্রকার স্বার্থের বন্ধনের অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়। এ বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি কাহারও নাই, কেননা ভাষা অশরীরী। শব্দ বহির্জগতে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনোজগতে চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী ভিত্তির উপরই আমরা সরস্বতীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করি।
৫.
যে সভার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি সেই সভাতে এই রাজশাহি শহরে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, আমাদের স্কুল-কলেজে বঙ্গভাষার সম্যক্ চর্চা হওয়া একান্ত কর্তব্য এবং আমি সে প্রস্তাবের সমর্থন করি। বঙ্গসন্তানের শিক্ষা যতদূর সম্ভব বঙ্গভাষাতেই হওয়া সংগত, এরূপ প্রস্তাব সে যুগের শিক্ষিত লোকদের মনঃপূত হয় নাই। এ প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই, অনেকে আবার অসম্ভবরূপ বিরক্তও হইয়াছিলেন। এ প্রস্তাবের প্রতি যে সেকালে কতদূর অবজ্ঞা দেখানো হইয়াছিল তাঁহার প্রমাণ, প্রকাশ্যে। কেহ এ কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। কবির কবিত্ব এবং বিদূষকের ভাড়ামি সুবুদ্ধি চিরকালই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। আজ মাতৃভাষার চর্চা করিতে বলিলে কাহারও ধৈর্যচ্যুতি হয় না, কেননা ইতিমধ্যে সে ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কোণে একটুখানি স্থান লাভ করিয়াছে। এমন কি, শ্ৰীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাষাণমূর্তির পাদপীঠে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে তাঁহার যত্নে এবং তাঁহার চেষ্টায়–The mother’s tongue has been put in the step-mother’s hall, অর্থাৎ বিমাতার আলয়ে মাতার রসনা স্থাপিত হইয়াছে। দেশসুদ্ধ লোক ইহা গৌরবের কথা মনে করিতেছেন। কিন্তু বিমাতার মন্দিরে মাতৃভাষা যে অদ্যাপি যথাযোগ্য স্থান লাভ করেন নাই, ঐ বিমাতৃভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিই তাঁহার পরিচয়। এবং উক্ত লিপি ইহাও প্রমাণ করিতেছে যে, ভাষাসম্বন্ধেও আত্মবশ হওয়াই সুখের এবং পরবশ হওয়াই দুঃখের কারণ। সত্য কথা এই যে, মাতৃভাষার সাহায্যেই আমরা যথার্থ ভাষাজ্ঞান লাভ করি এবং সে জ্ঞানের অভাবে আমরা পরভাষাও যথার্থরূপে আয়ত্ত করিতে পারি না। যেদিন আমাদের সকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা প্রাধান্য লাভ করিবে এবং ইংরাজি ভাষা দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে সেইদিন বঙ্গসন্তান যথার্থ শিক্ষালাভের অধিকারী হইবে।
এক দিন যেমন বাংলা পড়িতে বলিলে অনেকে মনে প্রমাদ গনিতেন, আজ তেমনি বাংলা লিখিতে বলিলে অনেকে মনে প্রমাদ গনেন। সেকালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, আমরা নবশিক্ষার আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি; একালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আমরা নবসাহিত্যের আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমাদের জাতীয় ভাষা যে এত হেয় যে, তাঁহার স্পর্শে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সব মলিন হইয়া যায়, এ কথা বলায় বাঙালি অবশ্য তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় দেন না, পরিচয় দেন শুধু তাঁহার বিজাতীয় নবশিক্ষার। যে কারণেই। হউক, অনেকে যে মাতৃভাষার পক্ষপাতী নহেন তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমি এই উপলক্ষেই পাইয়াছি। যেদিন আমি এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হই সেদিন আমার কোনো শুভার্থী বন্ধু আমাকে সতর্ক করিয়া দেন যে, এ সভাস্থলে ‘বীরবলী ঢং চলবে না। যে-কোনো সভাতেই হউক-না কেন, বিদূষকের আসন যে সভাপতির আসনের বহু নিয়ে সে জ্ঞান যে আমার আছে তাহা অবশ্য আমার বন্ধুর অবিদিত ছিল না। অপর পক্ষে আমার উপর তাঁহার এ ভরসাটুকুও ছিল যে, এই সুযোগে আমি এই উচ্চ আসন হইতে সভার গাত্রে বীরবলিক অ্যাসিড নিক্ষেপ করিব না। আসলে তিনি এ ক্ষেত্রে আমাকে বীরবলের ভাষা ত্যাগ করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কেননা সে ভাষা আটপহুরে, পোশাকি নয়। সভ্যসমাজে উপস্থিত হইতে হইলে সমাজসম্মত ভদ্রবেশ ধারণ করাই সংগত, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সে বেশ যতই অনভ্যস্ত হউক-না কেন। আমি তাঁহার পরামর্শ অনুসারে ‘পররুচি পরনা’–এই বাক্য শিরোধার্য করিয়া এ যাত্রা সাধুভাষাই অঙ্গীকার করিয়াছি। কেননা সাধুভাষা যে ধোপদুরস্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহাতে একটুওরং নাই এবং অনেকখানি মাড় আছে, ফলে ইহা স্বতঃই ফুলিয়াও উঠে এবং খড়খড়ও করে। আশা করি, এ সন্দেহ কেহ করিবেন না যে, এই বেশপরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে আমার মতেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সময়োচিত বেশ ধারণ করা আমাদের সমাজের সনাতন প্রথা। আমরা কৈশোরের প্রারম্ভে অন্ততঃ তিন দিনের জন্যও কর্ণে সুবর্ণকুণ্ডল এবং দেহে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তকে ঝুলি-স্কন্ধে দণ্ডহস্তে নগ্নপদে ভিক্ষা মাগি। এই আমাদের প্রথম সংস্কার। তাঁহার পর যৌবনের প্রারম্ভে অন্ততঃ এক দিনের জন্যও অমর। রাজবেশ ধারণ করিয়া তক্ত-রাঙায় চড়িয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া পাত্রমিত্ৰসমভিব্যাহারে কনে নামক একটি অবলা প্রাণীর গৃহাভিমুখে রণযাত্রা করি। ইহাই আমাদের দ্বিতীয় সংস্কার। আমরা যখন রাজাও সাজিতে জানি, ব্রহ্মচারীও সাজিতে জানি, তখন সভ্য সাজা তত আমাদের পক্ষে অতি সহজ। জীবনে সভ্যতার সাজ খোলাই কঠিন, পরা সহজ।
৬.
ভাষা সাহিত্যের মূল উপাদান, সুতরাং সাহিত্যপরিষদে ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখকের ভাষার সৌন্দর্যের দ্বারাই। পাঠকের মনোরঞ্জন করেন এবং ভাষার শক্তির দ্বারাই পাঠকের মন হরণ করেন। কাজেই কোনো লেখক আর সাধ করিয়া শ্রীহীন এবং শক্তিহীন ভাষা ব্যবহার করেন না। আমরা যে লেখায় মৌখিক ভাষার পক্ষপাতী তাঁহার কারণ, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষা রূপে-যৌবনে তথাকথিত সাধুভাষা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কথা আমি নানা সময়ে নানা স্থানে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছি। আত্মমত সমর্থনের জন্য কখনো বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, বিরুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য কখনো বা তাঁহার উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছি। এ স্থলে সেসকল কথার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, পুনরুক্তি ওকালতিতে যে পরিমাণে সার্থক, সাহিত্যে সেই পরিমাণে নিরর্থক।
আপাততঃ আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এই সাধুভাষার জন্মবৃত্তান্তের পরিচয় দিতেছি, তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন যে ইহার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা কেবলমাত্র উজ্জ্বলতা কি আর-কিছু।
বাংলার প্রাচীন সাহিত্য আছে কিন্তু সে সাহিত্য পদ্যে রচিত, গদ্যে নয়। আজ প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে আমাদের গদ্যসাহিত্য জন্মলাভ করে, এবং সাধুতা এই সাহিত্যেরই ধর্ম। শতবর্ষ পরমায়ু, বিধির এই নিয়মানুসারে, এ সাহিত্যের এখন পরিণত দেহ ত্যাগ করিয়া নবকলেবর ধারণ করা উচিত।
সে যাহা হউক, এ সাহিত্য জাতীয় মন হইতে গড়িয়া উঠে নাই। ইংরেজ রাজপুরুষদের ফরমায়েশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকর্তৃক নিতান্ত অযত্নে ইহা গঠিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব, দুই হিসাবেই এই শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত প্রবোধ চন্দ্রিকা ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং প্রথম স্তবকে মুখবন্ধে ভাষাপ্রশংসা নাম প্রথম কুসুমং’-এর শেষাংশে লিখিত আছে যে–
গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত অবোধ চন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।
বঙ্গভাষা সম্বন্ধে বিদ্যালংকারমহাশয়ের ধারণা কিরূপ ছিল তাঁহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন।
অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতিশীঘ্রতাপ্রযুক্ত উপৰ্য্যধোভাবাবস্থিত কোমলতর বহুল কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত। এতদ্রুপে প্ৰবৰ্তমান সকল ভাষাহইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা বহু বর্ণময়ত্ব প্রযুক্ত এক দ্ব্যক্ষর পশুপক্ষিভাষাহইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্য ভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তমা এই নিশ্চয়।
উক্ত ভাষা যে অম্মদাদির ভাষা নহে, তাহা বলা বাহুল্য। এবং এই ভাষায় অভিনব যুবক সাহেবজাতেরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কোনোই দুঃখ নাই; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অভিনব যুবক বঙ্গজাতেরাও যুগে যুগে এইরূপ ভাষা উত্তম। ভাষা হিসাবে শিক্ষা করিয়াছেন। কেননা এই রচনাই সাধুভাষার প্রথম সংস্করণ, এবং বিলাতি ছাপাখানার ছাপমারা এই ভাষাই কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়া আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আমি দোষী করি না। তাঁহাদের বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার কোনোরূপ অভিপ্রায় ছিল না; কেননা দেশি ভাষায় যে কোনোরূপ শাস্ত্র রচিত হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণার বহিভূত ছিল।
ফলতঃ, এসকল বিদ্যালংকারমহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দোমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া বিদ্যালংকারমহাশয় এই কিম্ভুতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ রচনায় কোনোরূপ যত্ন কোনরূপ পরিশ্রমের লেশমাত্রও নিদর্শন নাই। বিদ্যালংকারমহাশয় নিজে কখনোই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দঃপাত করিলে তাহা যে বাংলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা তিনি এক দিকে যেমন সাধুভাষার আদি লেখক, অপর দিকেও তিনি তেমনি চলতি ভাষারও আদর্শ লেখক। নিম্নে তাঁহার চলতি ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—
মোরা চাস্ করিব ফসল পাবে। রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবে। ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসূর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কী তুষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালালি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাঁইজ করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেঁচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস খাঁটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি।…শীতের দিনে কাঁথা খানী ছালিয়া গুলিকের গায় দি আপনার। দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়লের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গা সীসা পিতলের বালা তাড় মল খাড়, গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে না এক আদ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দাম বুঝিয়া লয় কড়া কপর্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদার তালুকদার জমীদারের পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বক্না কাঁথা পাতরা চুপড়ী কুলা ধূচনীপৰ্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সৰ্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না কতো বা সাধ্য সাধনা করি হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ ওরে পোড়া বিধাতা আমারদের কপালে এত দুঃখ লেখিস তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি।
এ ভাষা অস্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাংলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্র জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্যরচনার উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই তাঁহার প্রমাণ। এই ভাষার গুণেই বিদ্যালংকারমহাশয়ের রচিত পল্লিচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এ বর্ণনাটি সাধু ভাষায় অনুবাদ কর, ছবিটি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। অপর পক্ষে বিদ্যালংকারমহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে পূর্বোধৃত উক্তিটি ভাষায় অনুবাদ কর, তাঁহার বক্তব্য কথা সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি বিদ্যালংকারমহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রী বৃদ্ধি করিত। কিন্তু তাহারা বিদ্যালংকারমহাশয়ের গৌড়ীয় রীতিকেই গ্রাহ করিয়া তাহাকে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের ত্যক্ত দায় আমরা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে লাভ করিয়া অদ্যাপি তাহাই ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। প্রবোধ চন্দ্রিকার তৃতীয় স্তবকের কুসুমগুলি মেঠো হইলেও স্বদেশি ফুল। আর প্রথম স্তবকের কুসুমগুলি শুধু কাগজের নয়, তুলোট কাগজের ফুল। অবাদ করিতে জানিলে কাঠগোলাপ বসরাই গোলাপে পরিণত হয়। কিন্তু কালের কবলে ছিন্নভিন্ন বিবর্ণ হওয়া ব্যতীত কাগজের ফুলের গত্যন্তর নাই।
৬.
কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, এই দুই ভাষার মিলনসূত্রেই বর্তমান সাধুভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ। বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতীয়, সুতরাং ইহাদের যোগাযোগে কোনোরূপ নূতন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। বহুকাল যাবৎ এ দুই পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবেই চর্চা করা হইয়াছিল। একের পরিণতি কালী সিংহ মহাশয়ের মহাভারতে, অপরের পরিণতি তাঁহার হুতোম প্যাচার নক্শায়। ইহার কারণও স্পষ্ট। হুতোমি ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করা মূর্খতা এবং মহাভারতের ভাষায় সামাজিক নক্শা রচনা করা ছন্নতা মাত্র।
যে ভাষা আসলে এক, জোর করিয়া তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই দুই ভাষা রচিত হয়। সে ভাঙা জোড়া লাগাইবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের মৌখিক ভাষা নিছক চাষার ভাষাও নহে, নিটোল সংস্কৃতও নহে। আমাদের মুখের ভাষায় বহু তৎসম শব্দ এবং বহু তদ্ভব শব্দ আছে। দেশীয় শব্দও যে নাই তাহা নহে, তবে তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয়। হয় তৎসম নয় তদৃভব শব্দ বর্জন করিয়া বাংলা লেখার অর্থ ভাষার উপর অত্যাচার করা; অকারণে অযথারূপে তাহাকে হয় স্ফীত করিয়া তোলা, নয় শীর্ণ করিয়া ফেলা। সুতরাং এ দুই পথের ভিতর কোনো মধ্যপথ রচনা করিবার কোনো আবশ্যকতা ছিল না; কেননা সে মধ্যপথ তত চিরকালই আমাদের মুখস্থ ছিল। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের ভার কতদূর সয়, মৌখিক ভাষার প্রতি কর্ণপাত করিলেই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জ্ঞান অর কাহারও থাক্ আর নাই থাক্, রামমোহন রায়ের ছিল।
৮.
তিনি তাঁহার বেদান্ত গ্রন্থের (খৃ ১৮১৫) ‘অনুষ্ঠানে’ লিখিয়াছেন যে—
প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে এভাষা সংস্কৃতের জেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের [sentence] অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হটাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যুনতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক…
সকল দেশেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষার যে ঐশ্বর্য আছে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষার তাহা নাই। সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা ধনে ও মনে সমান দরিদ্র। তাঁহাদের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং ভাষাও সংকীর্ণ। যদি ভদ্রসমাজের মৌখিক ভাষা সাধুভাষা হয়, তাহা হইলে সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী ভাষা। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, লৌকিক ভাষা এই সাধুভাষার অন্তভূত, বহিভূত নয়। রামমোহন রায় যাহাকে ‘গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য’ শব্দ বলেন সেই শব্দসমূহই সকল ভাষার মূলধন।।
রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, এ ভাষা সংস্কৃতের অধীন। এ কথাও আমরা মানিতে বাধ্য। কিন্তু সে অধীনতা অভিধানের অধীন, ব্যাকরণের নয়; এই সত্যটি মনে রাখিলে ব্যাকরণ আমাদের নিকট বিভীষিকা হইয়া দাঁড়ায় না। ভাষার স্বাতন্ত্র যে তাঁহার গঠনের উপর নির্ভর করে, এ সত্য রামমোহন রায়ের নিকট অবিদিত ছিল না। তাঁহার মতে ভিন্ন দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়। অতএব এক ভাষা অপর ভাষার ব্যাকরণের অধীন হইতে পারে না।
আমরা যখন দৈনিক জীবনের অন্নবস্ত্রের সুখদুঃখের অতিরিক্ত কোনো বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন সংস্কৃত অভিধানের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। নানা ভাষার মধ্যে শব্দের পরস্পর-আদানপ্রদান আবহমানকাল সভ্যসমাজে চলিয়া আসিতেছে। আবশ্যকমত ঐরূপ শব্দ আত্মসাৎ করায় ভাষার কান্তি পুষ্ট হয়, স্বরূপ নষ্ট হয় না। নিতান্ত বাধ্য না হইলে এ কাজ করা উচিত নয়, কেননা পরভাষার শব্দ আহরণ কিংবা হরণ করা সর্বত্র নিরাপদ নহে। শব্দের আভিধানিক অর্থ তাঁহার সম্পূর্ণ অর্থ নয়, আভিধানিক অর্থে ভাবের আকার থাকিলেও তাঁহার ইঙ্গিত থাকে না। লৌকিক শব্দের আদ্যোপান্ত বর্জন এবং অপর ভাষার অন্বয়ের অনুকরণেই ভাষার জাতি নষ্ট হয়। মৌখিক ভাষার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবার জো নাই। সুতরাং শিক্ষিত লোকের সবল অত্যাচার লিখিত ভাষাকেই নীরবে সহ্য করিতে হয়।
রামমোহন রায় যে মৌখিক ভাষার উপরেই তাঁহার রচনার ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রমাণ তাঁহার ব্যবহৃত পদসকল অবৈধসন্ধিবদ্ধ কিংবা সমাসবিড়ম্বিত নহে। তিনি জানিতেন যে—
সংস্কৃত সন্ধিপ্রকরণ ভাষায় উপস্থিতি করিলে, তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়;… সমাস সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে—
এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আইসে না।
তাঁহার মতে ‘হাতভাঙা’, ‘গাছপাকা’ প্রভৃতি পদই বাংলা সমাসের উদাহরণ। তাঁহার পরবর্তী লেখকেরা যদি এই সত্যটি বিস্মৃত না হইতেন তবে তাহারা বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃতের জাগ দিয়া পাকাইতে চাহিতেন না এবং হাতভাঙা পরিশ্রম করিয়া দাতভাঙা সমাসের সৃষ্টি করিতেন না। তিনি মৌখিক ভাষার সহজ সাধুত্ব গ্ৰাহ করিয়াছিলেন বলিয়া বানান-সমস্যারও অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত রীতিঅনুসারেই লিখিত হওয়া কর্তব্য এবং তদ্ভব ও দেশীয় শব্দের বানান তাঁহার উচ্চারণের অনুরূপ হওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ যে স্থলে শ্রুতিতে-স্মৃতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে স্মৃতি মান্য এবং বাংলা শব্দ সম্বন্ধে শ্রুতি মান্য। রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্যের যে সহজ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন সকলে যদি সেই পথের পথিক হইতেন তাহা হইলে আমাদের কোনোরূপ আক্ষেপের কারণ থাকিত না।
কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাঁহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে inodern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়। সুতরাং আমাদের দেশে ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গেই সাহিত্যে পণ্ডিতি যুগের অবসান হইল এবং ইংরেজি যুগের সূত্রপাত হইল। ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শেই আমরা বঙ্গসাহিত্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মিল্টন না পড়িলে বাঙালি মেঘনাদবধ লিখিত না, স্কট না পড়িলে দুর্গেশনন্দিনী লিখিত না এবং বায়রন না পড়িলে পলাশীর যুদ্ধ লিখিত না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল। ফলে বঙ্গসাহিত্য তাঁহার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আবার হারাইয়া বসিল। এই ইংরেজিনবিশ লেখকদিগের হস্তে বঙ্গভাষা এক নূতন মূর্তি ধারণ করিল। সংস্কৃতের অনুবাদ যেমন পণ্ডিতদিগের মতে সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইত, ইংরেজির কথায় কথায় অনুবাদ তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এই অনুবাদের ফলে এমন বহু শব্দের সৃষ্টি করা হইল যাহা বাঙালির মুখেও নাই এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই। এবং এইসকল কষ্টকল্পিত পদই এখন বঙ্গসাহিত্যের প্রধান সম্বল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এইসকল নব শব্দ গড়িবার কোনোই আবশ্যকতা ছিল না। সংস্কৃত দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে অলংকারে যথেষ্ট শব্দ আছে, যাহার সাহায্যে আমরা আমাদিগের নবশিক্ষালব্ধ সকল মনোভাব বঙ্গভাষার জাতি ও প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারি। আমরা তথাকথিত সাধুভাষার বিরোধী, কেননা আমাদের বিশ্বাস বঙ্গভাষা ব্রাত্য-সংস্কৃতও নহে, শাপভ্রষ্ট ইংরেজিও নহে। এই কারণে আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, কারণ সে ভাষা সহজ সরল সুঠাম এবং সুস্পষ্ট।
সুতরাং আমাদের এ চেষ্টা যে মাতৃভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক, এ অভিযোগের কোনোরূপ বৈধ কারণ নাই। যদি কেহ বলেন যে, ‘মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ, সুতরাং সে পথ অনুসরণ না করা ধৃষ্টতামাত্র, তাঁহার উত্তরে আমরা বলিব, বঙ্গসাহিত্যের মহাজনেরা যুগভেদ এবং শিক্ষাভেদ অনুসারে নানা বিভিন্ন পথের পথিক। দর্শনের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও মার্গভেদ আছে; আমাদের পূর্ববর্তী মহাজনেরা এই ভাষা লইয়া এক্সপেরিমেন্ট করিয়াছেন; সুতরাং নূতন এক্সপেরিমেন্ট করিবার অধিকার আমাদের আছে। গদ্যসাহিত্যের বয়স এখন সবে এক শ বৎসর, কাজেই তাঁহার পরীক্ষার বয়স আজও পার হয় নাই। টোলের ও কলেজের বাহিরে যে ভাষা মুখে মুখে চলিতেছে, সে ভাষার অন্তরে কতটা শক্তি আছে সে পরীক্ষা আজ পর্যন্ত করা। হয় নাই। আমরা সেই পরীক্ষা করিতে চাই। লোকে বলে, যখন প্রকৃব্রিটিশ যুগে গদ্য ছিল না তখন গত শতাব্দীর গদ্যই আমাদের একমাত্র আদর্শ। আমরা নিত্য যে ভাষায় কথাবার্তা কই তাঁহারই নাম যে গদ্য, এ সত্য মোলিয়েরের নাটকের নিরক্ষর ধনী বণিকের জানা ছিল না, কিন্তু আমাদের আছে। সাহিত্যে সেই সনাতন আদর্শই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।
আমি ভাষা সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম তাঁহার কারণ, এইরূপ সভাসমিতিতে সাহিত্যের যাহা সাধারণ সম্পত্তি তাঁহার আলোচনা এবং তাঁহার বিচার হওয়াই সংগত।
৯.
সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ভাষার নাম ‘কাব্যশরীর’। কিন্তু এ শরীর ধরাছোয়ার মত পদার্থ নয় বলিয়া যাঁহারা এ পৃথিবীতে শুধু স্কুলের চর্চা করেন, সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের চিরদিনই একটি আন্তরিক অবজ্ঞা থাকে, এবং ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অর্বাচীন বঙ্গসাহিত্যই বিশেষ করিয়া অবজ্ঞার সামগ্রী হইয়াছিল। এই বিরাট কুসংস্কারের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি ও সাহস পূর্বে ছিল কেবলমাত্র দু-চারি জন ক্ষণজন্মা পুরুষের। কিন্তু সাহিত্যচর্চা যে জীবনের একটি মহৎ কাজ, এ ধারণা যে আজ বাঙালির মনে বদ্ধমূল হইয়াছে তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সম্মিলনী। আমাদের নবশিক্ষার প্রসাদে আমরা জানি যে, সাহিত্য জাতীয়-জীবন-গঠনের সর্বপ্রধান উপায়, কেননা সে জীবন মানবসমাজের মনের ভিতর হইতে গড়িয়া উঠে। মানুষের মন সতেজ ও সজীব না হইলে মানবসমাজ ঐশ্বর্যশালী হইতে পারে না। যে মনের ভিতর জীবনীশক্তি আছে তাঁহার স্পর্শেই অপরের মন প্রাণলাভ করে এবং মানুষে একমাত্র শব্দের গুণেই অপরের মন স্পর্শ করিতে পারে। অতএব সাহিত্যই একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র। আমাদের সামাজিক জীবনের দৈন্য জগৎবিখ্যাত এবং সে দৈন্য দূর করিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যগ্র। এই কারণেই। শিক্ষিত লোকমাত্রেরই দৃষ্টি আজ সাহিত্যের উপর বদ্ধ। সাহিত্যই আমাদের প্রধান ভরসাস্থল বলিয়াই বর্তমান সাহিত্যের প্রতি আমাদের অসন্তোষও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে। এ অসন্তোষের কারণ এই যে, লোকে সাহিত্যের নিকট যতটা আশা করে, প্রচলিত সাহিত্য সে আশা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। কাজেই নানা দিক হইতে নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে নানা লোকে এই শিশু সাহিত্যের উপর আক্রমণ করিতেছেন। এইসকল সমালোচনার মোটামুটি পরিচয় নেওয়াটা অবশ্যক।
১০
আজ আমরা সকলে মিলিয়া এ সাহিত্যের জাতিবিচার করিতে বসিয়াছি। এ নবপণ্ডিতের বিচার, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিচার নহে। কেননা বঙ্গসাহিত্য স্বজাতীয় কি বিজাতীয়, সে বিচার ইউরোপীয় শাস্ত্রের অধীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের পুষ্পচয়ন করি আর না করি, ইউরোপীয় শাস্ত্রের পল্লব যে গ্রহণ করি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের নব সমালোচকেরা প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত। এক দলের অভিযোগ এই যে, নবসাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা প্রাচীন নয়। অপর দলের অভিযোগ এই যে, বর্তমান সাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা লৌকিক নহে।
শ্ৰীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গত দুই বৎসর ধরিয়া লোকারণ্যে এই বলিয়া রোদন করিতেছেন যে, দেশের সর্বনাশ হইল, সুকুমার সাহিত্য মারা গেল। তাঁহার আক্ষেপ এই যে, তাঁহার কথায় কেহ কান দেয় না, কেননা বাঙালি আজ তাঁহার মতে–
মস্তিস্কের তীব্র চালনাগুণে পাইতেছে জ্ঞানবিজ্ঞান বিদ্যাদর্শন পুরাবৃত্ত ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব জীবতত্ত্ব; হারাইতে বসিয়াছে দয়ামায়া শ্রদ্ধাভক্তি স্নেহমমতা কারুণ্যআতিথ্য আনুগত্য শিষ্যত্ব। আমরা কোমলপ্রাণ বাঙালি, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোমলতা হারাইয়া বুঝি-বা সর্বস্ব হারাইয়া ফেলি।
বাঙালির হৃদয়ের রক্ত সব যে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য বাঙালির জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তবে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত এ যুগে যে সাহিত্য রচনা করা যাইতে পারে না, এ কথা নিশ্চিত। সরকারমহাশয় প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষপাতী, কেননা তাঁহার বিশ্বাস, অতিনিকট-অতীতে–
বাঙালি গ্রামে গ্রামে পালোয়ান বাগদি গোপ চণ্ডাল প্রহরী রাখিয়া আপনাদের বিত্তস্বত্ব রক্ষা করিত
এবং তাঁহার প্রধান কাজ ছিল–
আহারান্তে খড়ের চণ্ডীমণ্ডপে খুটি হেলান দিয়া মুটকলমে ইতিহাস পুরাণ অবলম্বনে পুঁথি লেখা।
এভাবে অবশ্য আমরা পুঁথি লিখিতে পারি না, কেননা আমাদের বিত্ত উপার্জন করিতে হয় বলিয়া আমরা আহারান্তে আপিসে যাই এবং পেন্-কলমে ইংরেজি ভাষাতে ছাইপাশ কত কি লিখি। কিন্তু সরকারমহাশয় কোথা হইতে এ সত্য সংগ্রহ করিলেন যে পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা আলস্যের স্বর্গ ছিল? যাঁহারা পুরাতত্ত্বের সন্ধানে ফেরেন, তাহারা তো অদ্যাবধি এ বাংলার সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। বোধ হয় সেই কারণেই ইতিহাস সরকারমহাশয়ের কোমল বাঙালি-প্রাণে এত ব্যথা দেয়। বাঙ্গালা-সাহিত্যে যে ইতিহাসের পর দরইতিহাস, তাঁহার পর ছে-ইতিহাস দাখিল হইতেছে, আবার ইদানীং সওয়ালজবাবুও যে আরম্ভ হইয়াছে ইহা অক্ষয়বাবুর নিকট, অর্থাৎ শ্ৰীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নিকট, একেবারেই অসহ্য। কেননা এ শ্রেণীর ইতিহাসরচনার জন্য মস্তিষ্কচালনার প্রয়োজন আছে। অপর পক্ষে সরকারমহাশয়ের রচিত পুরাবৃত্ত কেবলমাত্র কল্পনা-চালনার দ্বারাই সৃষ্ট হয় এবং তাঁহার গঠনে কিংবা পঠনে বাঙালির কোমলতা হারাইবার কোনো আশঙ্কা নাই। আমি সরকারমহাশয়ের মতামত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, কেননা নানা দিক হইতে ইহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এ মত সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এসকল কথার মূল্য যে কত, তাহা নির্ধারণ করিতে কোনোরূপ মস্তিষ্কচালনার আবশ্যকতা নাই। বঙ্গসাহিত্য যতই শিশু হউক-না কেন, আমার বিশ্বাস, এরূপ আক্রমণে তাহ মারা যাইবে না।
১১.
অপর শ্রেণীর সমালোচকেরা আধুনিক কাব্যসাহিত্যের বিরোধী। ইহাদের। মতে সে সাহিত্য নেহাত বাজে, কেননা তাহা সমাজের কোনো কাজে লাগে না। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য কাব্যসকল যদি সরকারমহাশয়ের বর্ণিত আলস্যজাত সুকুমার সাহিত্য হয়, তাহা হইলে সে কাব্য যে সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং সর্বথা উপেক্ষণীয় সে বিষয়ে আর দ্বিমত নাই। সরকারমহাশয়ের অভিযোগ এই যে, বর্তমান সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটাইতেছে; ইহাদের অভিযোগ এই যে, সে সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের উন্নতিসাধন করিতেছে না। এ সাহিত্য লোকশিক্ষার সহায় নয়, কেননা ইহা লৌকিক নয়, অতএব ইহা জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী নয়।
এ যুগের সাহিত্য যে লৌকিক নহে তাহা সকলেই জানেন, কেননা এ সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে-গড়া সাহিত্য। আমাদের সাহিত্য যদি এই কারণে নিরর্থক হয়, তাহা হইলে তাঁহার এই সমালোচনা আরও বেশি নিরর্থক। শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত লোকের মনের প্রভেদ বিস্তর। এই পার্থক্য যদি দোষের হয়, তাহা হইলে এ দেশে শিক্ষার পাট উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষিত লোকের রচিত সাহিত্যে শিক্ষিত মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই শ্রেণীরই সাহিত্য। শকুন্তলা, হ্যামলেট, ডিভাইন কমেডিয়া প্রভৃতি স্বল্প বুদ্ধি এবং অল্পজ্ঞানের যোগাযোগে রচিত হয় নাই। মনেরও উপযুপরি নানা লোক আছে এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মানসিক ঊর্ধ্বলোকেরই বস্তু। জাতির মনকে লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যাওয়াই সাহিত্যের ধর্ম। কামলোক হইতে রূপলোকে উঠিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষার আবশ্যক, সাধনার আবশ্যক। কবি যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অপরের উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক। মনোজগতে অমনি-পাওয়া বলিয়া কোনো পদার্থ নাই, সবই দেওয়া-নেওয়ার জিনিস। এ যুগে এ দেশে যদি এমন কাব্য রচিত হইয়া থাকে যাহা সকল দেশের শ্রেষ্ঠ মনের পূজার সামগ্রী, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের যে কোনো সার্থকতা নাই, এরূপ কথার কোনো অর্থ থাকে না। বিশ্বমানবের কাছে আমাদের কাব্যসাহিত্য যে সে-মর্যাদা লাভ করিয়াছে তাহা তো সর্বজনবিদিত। ইউটিলিটেরিয়ানিজমের সাহায্যে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা যায় না। সাহিত্যের অবনতির দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন করা যায় না। ফাউস্টের প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা-তৃতীয়ভাগ নহে বলিয়া জর্মান পেট্রিয়টিজম সে কাব্যের বিরুদ্ধে কখনো খড়্গহস্ত হয় নাই। প্রতিভাশালী লেখকেরা যে, লোকশিক্ষক নহেন তাঁহার কারণ, তাহারা দুনিয়ার শিক্ষকদিগের শিক্ষক।
১২.
লোকরচিত কিংবা লোকপ্রিয়, এ দুই অর্থে ই লৌকিক সাহিত্য গান ও গল্পের সাহিত্য। সে গানের বিষয় দৈনিক জীবনের সুখ ও দুঃখ, এবং সে গল্পের বিষয় দৈনিক জীবনের বহিভূত আশ্চর্যকর ঘটনাবলী। গল্প ও গুজবে মিলিয়া যে আজগুবি ব্যাপারের সৃষ্টি হয় তাহাই জনসাধারণের চিরপ্রিয়। গীতিকবিতা এবং রূপকথাই লোকসাহিত্যের চিরসম্বল। এ সাহিত্য আমাদের নিকট তুচ্ছ নয়, কেননা আমরাও মানুষ এবং এইরূপ সুখদুঃখের আমরাও সমান অধীন। গল্প শুনিতে আমরাও ভালোবাসি এবং রূপকথার মায়া আমরাও কাটাইতে পারি না। আমাদের রচিত উপন্যাস-নবদ্যাসাদিতেও যদি রূপ না থাকে তাহা হইলে তাহা কথা বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হউক, আমাদের কল্পনা তাঁহার সীমা লঙ্ঘন করিতে সদাই উৎসুক। আমাদের দর্শনবিজ্ঞানের কথাও কতক অংশে স্বরূপকথা, কতক অংশে রূপকথা; এবং এই কারণেই তাহা মানুষের শুধু মন নয়, হৃদয়ও আকর্ষণ করে। ইভলিউশনের ইতিহাসের ন্যায় বিচিত্র কথা কোনো রাজারানীর উপাখ্যানেও নাই। আমাদের বিজ্ঞানের আলয় আমাদের নিকটেও এক হিসাবে জাদুঘর। জনসাধারণের সহিত কৃতবিদ্য লোকের প্রভেদ এই যে, তাঁহাদের নিকট তাহা জাদুঘর ব্যতীত আর কিছুই নয়। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং অবৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ভিতর ব্রাহ্মণশূদ্র-প্রভেদ। শূদ্র-সাহিত্যে দ্বিজের সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু দ্বিজসাহিত্যে শূদ্রের অধিকার আংশিক মাত্র। শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার নাই, অধিকার আছে শুধু পুরাণ-ইতিহাসে। কারণ এ সাহিত্য গীত হয় এবং ইহা অপূর্ব জল্পনা এবং অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সাহিত্যচর্চায় যে অধিকারীভেদ আছে তাহা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য লৌকিক না হইলেও যে লোকায়ত্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান এবং বঙ্কিমের গল্প জনসাধারণের আদরের সামগ্রী হইতে পারে, কিন্তু সমালোচকদের আলোচনা-গবেষণা-প্রবন্ধ-নিবন্ধাদিই তাঁহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য।
১৩.
পূর্বোক্ত সমালোচকেরা বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ কীর্তিগুলির প্রতিই বিমুখ। যদি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব করিবার মত কোনো বস্তু থাকে, তাহা হইলে তাহা বঙ্কিমের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের নব্য ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্ব। কিন্তু এই-জাতীয় সাহিত্যই তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ, কেননা তাহা জাতীয় নয়। কিন্তু যাহা, জাতীয় হউক বিজাতীয় হউক, সাহিত্যই নয় তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করেন না। সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্য রচনা করিবার রহস্য ও কৌশল যদি সমালোচকদিগের জানা থাকে, তবে তাহারা স্বয়ং যে সে-সাহিত্য রচনা করেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। কেননা বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যই এই যে, দু-একটি প্রথমশ্রেণীর লেখক বাদ দিলে বাদবাকি তৃতীয়-চতুর্থশ্রেণীভুক্তও নন। ইউরোপের যে-কোনো দেশের হউক, বর্তমান সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে এ সত্য সকলের নিকটই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। এ দৈন্য ইচ্ছা করিলেই আমরা। ঘুচাইতে পারি। সাহিত্যের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণী অধিকার করিবার জন্য অসাধারণ প্রতিভা চাই না, চাই শুধু যত্ন এবং পরিশ্রম। দণ্ডী বলিয়াছেন–
ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসনা
গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভূতম্।
শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা
ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্।।
অর্থাৎ অদ্ভুত প্রতিভা এবং প্রাক্তন সংস্কারের অভাব সত্ত্বেও আমরা যদি সযত্নে সরস্বতীর উপাসনা করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব না।
বাঙালি জাতির হৃদয়ে রস আছে মস্তিষ্কে তেজ আছে, তবে যে আমাদের সাধারণ সাহিত্য যথোচিত রস ও শক্তি -বঞ্চিত তাঁহার জন্য দোষী আমাদের নবশিক্ষা। আমাদের ত্রুটি কোথায় এবং কিসের জন্য, সংক্ষেপে তাঁহার উল্লেখ করিতেছি।
মানুষের সকল চিন্তার, সকল ভাবের, একটি-না-একটি অবলম্বন আছে। বস্তুজ্ঞানের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত, সে বস্তু মনোজগতের হউক আর বহির্জগতেরই হউক। বিদ্যালয়ে আমরা কোনো বিশেষ বস্তুর পরিচয় লাভ করি না, কিন্তু অনেক নাম শিখি। আমরা ইংরেজি ভাষায়, ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষিত হই, অথচ ইংরেজি জীবনের সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয়ও নাই, কাজেই সে শিক্ষার প্রসাদে আমরা সঞ্চয় করি শুধু কথা। আমরা কংক্রিটের জ্ঞান হারাই এবং তাঁহার পরিবর্তে পাই শুধু অ্যাবস্ট্রাকশন্স। ফুল বলিয়া কোনো পদার্থ জগতে নাই, আছে শুধু ভাষায়। পৃথিবীতে আছে শুধু যুথী জাতী মল্লিকা মালতী প্রভৃতি। বর্ণে গন্ধে আকারে একটি অপরটি হইতে বিশিষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহারা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। হথর্ন লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেট আমাদের নিকট নাম মাত্র। এ নাম আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে না, আমাদের মনে কোনোরূপ পূর্ব স্মৃতি জাগরূক করে না, কাজেই ফুলমাত্রেই আমাদের নিকট flower হইয়া উঠে। অর্থাৎ অদৃষ্ট বর্ণ, অজ্ঞাত আকার এবং অননুভূত গন্ধের একটি নামাশিত সমষ্টিমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি জাতিবাচক সম্বন্ধবাচক এবং ভাববাচক শব্দ সংগ্রহ করি। অথচ সে জাতি সে সম্বন্ধ সে ভাব যে কাহার, তাঁহার কোনো খোঁজ নাই। কাজেই আমরা মানুষের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া মনুষ্যত্বের বিচার করিতে বসি। অথচ পৃথিবীতে মানুষ আছে কিন্তু মনুষ্যত্ব নামক জাতিবাচক শব্দের পশ্চাতে কোনো পদার্থ নাই। সকল বিশেষের সকল বিশেষণ বাদ দিয়াই আমরা সর্বনাম লাভ করি। এই সর্বনামেরও অবশ্য সকল ভাষাতেই স্থান আছে। কিন্তু এরূপ পদের ব্যবহারের সার্থকতা সেই স্থলেই আছে যে স্থলে মুহূর্তের মধ্যে আমরা সর্বনামকে ভাঙাইয়া বিশেষ্যে পরিণত করিতে পারি। যে সর্বনাম নাম মাত্র, তাহা কেবল অদৃষ্টার্থ ধ্বনিমাত্র। আমরা আমাদের শিক্ষালব্ধ অ্যাবস্ট্রাক্শন্ লইয়া সাহিত্যে কারবার করি বলিয়াই আমাদের লেখায় না আছে, দেহ, না আছে প্রাণ। ইউরোপীয় সাহিত্যও আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না, আমরা সদলবলে ইউরোপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিব না। তবে এ রোগের ঔষধ কি? আমার বিশ্বাস, আমাদের চতুস্পার্শ্বস্থ রিয়ালিটির প্রতি মনোযোগ দিলে আমরা এই অ্যাস্ট্রাকশনের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইব। অনুভূতিই যে সকল জ্ঞানের মূল, এই সত্যের সম্যক উপলব্ধি না হইলে আমাদের রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বরসার হইতে বাধ্য। আমাদের দেশেও ফুলফল গাছপালা আছে, নরনারী ধনীদরিদ্র আছে। এইসকল বস্তুবিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের উপরেই যথার্থ বঙ্গসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণেই আমি সাহিত্যে প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী। যাঁহারা চিরজীবন প্রকৃতির সহিত মুখোমুখি করিয়া বাস করেন, আশা করা যায়, তাঁহাদের রচনায় এই রিয়ালিটির রূপ ফুটিয়া উঠিবে। আমি খাঁটি বাংলা ভাষার পক্ষ পাতী, কারণ সে ভাষা কংক্রিট ( বিশেষসংজ্ঞক) শব্দবহুল। প্রবোধ চন্দ্রিকা হইতে আমি খাঁটি বাংলার যে নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, প্রায় প্রতি শব্দই কংক্রিট। এই বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে সংগৃহীত সামান্য ভাবগুলিও যথাযোগ্য প্রয়োগ করিতে পারি না। যে ভাব জীবনসংগ্রামে আমাদের হাতে অস্ত্র হওয়া উচিত, তাহাকে হয়তো আমরা ভূষণস্বরূপে দেহে ধারণ করি। এবং যাহা ভূষণমাত্র, তাঁহারও আমরা অযথা ব্যবহার করি। ইউরোপের পায়ের মূল গলার হারস্বরূপে বঙ্গসরস্বতীকে কণ্ঠস্থ করিতে দেখা গিয়াছে।
পরীক্ষা ব্যতীত কোনো বস্তুরই সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু। কোনো বস্তুকেই পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। ইহাও আমাদের শিক্ষার দোষে। দিব্যাবদানে দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধযুগে জম্বুদ্বীপে কুলপুত্রদিগকে অষ্টবিধ বস্তু পরীক্ষা করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এ যুগে স্কুলকলেজে আমরাই পরীক্ষিত হই, কিছুই পরীক্ষা করিতে শিখি না। আমরা যদি রত্ন পরীক্ষা করিতে শিখিতাম তাহা হইলে আমরা সাহিত্যে কাচকে মণি এবং মণিকে কাচ বলিতে ইতস্ততঃ করিতাম। আমাদের পক্ষে পরীক্ষা-বিদ্যা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা নানা দেশের নানা যুগের নানা শাস্ত্র পড়ি অথচ দেশি বিদেশি নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কোটি গ্রাহ্য এবং কোটি অগ্রাহ্য, তাহা স্থির করিতে পারি না। আমরা বর্তমান ইউরোপ এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলি— ‘ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন মোহয়সি মাম্। এ অবস্থায় সকল বিষয়েরই যে দুটি দিক আছে, এইমাত্র আমরা জানি; কিন্তু কোটি যে তার দক্ষিণ আর কোটি যে বাম, সে জ্ঞান আমাদের নাই। মাসেরও যে দুটি পক্ষ আছে, এই জ্ঞান আমরা পঞ্জিকা হইতেও সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার কোটি কৃষ্ণ এবং কোন্টি শুক্ল তাহা জানিবার জন্য চোখ খুলিয়া দেখা আবশ্যক।
বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে মহা আশার কথা এই যে, অন্ততঃ ইহার একটি শাখায় এই পরীক্ষার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির নিকট ইহার জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। সুহৃর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ বরেন্দ্রমণ্ডলের ভূগর্ভে লুক্কায়িত দেবদেবীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় খাড়া করিয়া আজ প্রশ্ন করিতেছেন, জেরা করিতেছেন। কেবলমাত্র জবানবন্দী লইয়াই তাহারা ক্ষান্ত হন না, আবশ্যকমত সওয়ালজবাবু করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত। এরূপ পরীক্ষাকার্যে বাঙালির কোমল প্রাণে ব্যথা দিতেও যে নব ঐতিহাসিকের কুণ্ঠিত নন, তাঁহার প্রমাণস্বরূপ আমি তাঁহাদের কৃত কার্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই–
মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া এক কৃষক একটি তাম্রপটুলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে তাহাকে সিন্দুরলিপ্ত করিয়া আমরণ পূজা করিয়াছিল।
এই তাম্রশাসনখানি ঐতিহাসিকদের হাতে পড়িয়া সিন্দুরচর্চিত এবং পূজিত হইতেছে না, পরীক্ষিত হইতেছে।
বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদেরও ইঁহাদের প্রদর্শিত পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে। তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ, ভূর্জপত্রে লিখিত এবং বিলাতি কাগজে মুদ্রিত লিপিকে সিরলিপ্ত করিয়া পূজা করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে লিপিমাত্রই, সে প্রাচীনই হউক আর অর্বাচীনই হউক, বাঙালির হাতে পরীক্ষিত হইবে। কেবলমাত্র লিপি পরীক্ষা করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব না। ধর্ম, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সমাজের মন, নিজের মন–এই সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিচারালয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইবে। এ বিচার কেবল দর্শনে-বিজ্ঞানে নয়, নাটকে-নভেলেও হইবে। কেননা বিদ্যার সহিত, সম্পর্কহীন সাহিত্য সভ্যসমাজে আদৃত হইতে পারে না। সমাজের সকল জ্ঞান সাহিত্যে কেন্দ্রীভূত এবং প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। যে কথা বিন পরীক্ষায় ডবলপ্রমোশন পায়, সে কথা ভবিষ্যতের সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে না। সত্যের স্পর্শ সহ্য করিবার অক্ষমতার নাম যদি কোমলতা হয়, তাহা হইলে জাতীয় মন হইতে সে কোমলতা দূর করিতে হইবে। কেননা ও কোমলতা দুর্বলতারই নামান্তর, এবং যুক্তিতর্কের উপর্যুপরি আঘাতে সে মনকে কঠিন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের সাহিত্যের সৌকুমার্য নষ্ট হইবার কোনো আশঙ্কা নাই।
ভবভূতি বলিয়াছেন, মহাপুরুষের মন যুগপৎ বজ্রকঠিন এবং কুসুমসুকুমার জাতীয় মহাপুরুষত্বলাভই সাহিত্যসাধনার ধ্রুবলক্ষ্য হওয়া কর্তব্য।
এই প্রসঙ্গে আমি বঙ্গসাহিত্যের আর-একটি ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিতে চাহি। আমাদের গদ্যের ভাষা ও ভাব দুইই শিথিলবন্ধ। আমাদের রচনায় পদ, বাক্য–কিছুই সুবিন্যস্ত নয় এবং আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বদ্ধ নয়। ইহা যে শক্তিহীনতার লক্ষণ তাহা বলা বাহুল্য। যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকলের পরস্পরসম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, সে দেহের শক্তিও নাই, সৌন্দর্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই গঠন রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের রচনা সুগঠিত হয় না, সেই ছন্দ রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।
ভাষার ন্যায় ভাবও রচনা করিতে হয়। আমাদের চিত্তবৃত্তি স্বতঃই বিক্ষিপ্ত। যাহা বিক্ষিপ্ত তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করা সাহিত্যের কাজ। মনের ভিতর যাহা অস্পষ্ট তাহাকে স্পষ্ট করা, যাহা নিরাকার তাহাকে সাকার করাই আর্টের ধর্ম।
যেসকল মনোভাব গ্রন্থিবদ্ধ নয়, তাঁহাদের বিশৃঙ্খল সমষ্টি সমগ্রতা নয়। চিন্তাগঠনের প্রণালীকেই আমরা লজিক বলি। লজিক এবং আর্টের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, গ্রীক সভ্যতাই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা আর্ট এবং লজিক, এই দুই এ সভ্যতার সর্ব প্রধান কীর্তি। প্রকরণভঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যে মহাদোষ বলিয়া গণ্য। আমাদের গদ্যরচনা যে এ দোষে অল্পবিস্তর দুষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। এ দোষ বর্জন করিবার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন আছে শুধু মনোযোগের। সাহিত্যের সাধনাও একরূপ যোগাভ্যাস। ধ্যানধারণা ব্যতীত এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ধ্যানধারণা করা আর না করা আমাদের ইচ্ছাধীন। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই আমরা আমাদের রচনা দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারি।
আমার বিশ্বাস, বাঙালি জাতির হৃদয়মনের ভিতর অপূর্ব শক্তি আছে। যে শক্তি আজ আংশিক ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিই আমাদের সকল সাধনার বিষয় হওয়া কর্তব্য। এই কারণেই আমি যে ভাষা ও যে ভাব সাহিত্যের সেই শক্তির পূর্ণবিকাশের বাধাস্বরূপ মনে করি, তাঁহার দূরীকরণের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছি।
এ যুগে নিজের মতকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ নিজের মনে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা, তাহা প্রকাশ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং যাঁহারা আমার মত গ্রাহ করিতে অক্ষম, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন বিনা বিচারে এ মতের প্রতি সাহিত্যরাজ্য হইতে নির্বাসনদণ্ড প্রচার না করেন। আমি একটিমাত্র সত্যকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সে সত্য এই যে, বাঙালি জাতির দেহে প্রাণ আছে। প্রাণের অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বাহ্যবস্তুর স্পর্শে তাহা সাড়া দেয়। আজ এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙালির মনের সকল অঙ্গ ইউরোপীয় সভ্যতার স্পর্শে যথোচিত সাড়া দিয়াছে। এই ধ্রুবসত্যের উপরেই সাহিত্য সম্বন্ধে আমার সকল মতামত প্রতিষ্ঠিত।
১৩২১ ফাল্গুন
কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত
কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত
সাহিত্যসমাজ মানুষের আর পাঁচ রকম সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী নয়। এ সমাজেও দলাদলি আছে, বকাবকি আছে, যুদ্ধবিগ্রহ আছে, জয়পরাজয় আছে। ইংরেজরা বলে Fight is the salt of existence। সাহিত্যের হাটে এ নুনের কারবার আমরা সবাই করি।
যখন কোনো জাতির অন্তরে কাব্যরস শুকিয়ে আসে তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, সাহিত্যিকদের পিত্ত সেই সঙ্গে প্রকুপিত হয়ে ওঠে; আর তখন সাহিত্য কি হওয়া উচিত, তাই নিয়ে মহা বাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। গত বর্ষের গ্রীষ্মকালে এ দেশের সাহিত্যসমাজ অকস্মাৎ মহা উত্তেজিত হয়ে ওঠে সাহিত্যের একটি গুণ কিংবা অগুণের বিচার নিয়ে। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ কি গুণ, এই সমস্যার মীমাংসা করতে অনেকেই বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। আমি এ বাগযুদ্ধে। যোগ দিই নি; কারণ, এ লড়াই ইউরোপের খৃস্টান সমাজ যুগ যুগ ধরে করে এসেছে, অথচ তার ফলে সাহিত্যের বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হয় না। অনেকে এ জাতীয় যুদ্ধকে সাহিত্যজগতের ধর্মযুদ্ধ মনে করেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, religious warএর প্রসাদে ধর্মরক্ষা হয় না।
সে যাই হোক, কাব্যজগতে এই শ্লীল-অশ্লীলতার বিচার আবহমানকাল যে চলে আসছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান গুণ তার শ্লীলতা নয়। এমনকি গত শতাব্দীর ইংরেজি মতে তা ঘোর অশ্লীল। হল Hall নামক জনৈক ইংরেজ ওরিয়েন্টালিস্ট বাসবদত্তার যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তার ভূমিকার প্রতি নজর দিলেই সমগ্ৰ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে সেকালের ইংরেজি ওরফে খৃস্টানি সাধু মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় সকলেই পাবেন।
২.
সংস্কৃত সাহিতা শ্লীলই হোক আর অশ্লীলই হোক, অশ্লীলতা যে কাব্যের একটি স্পষ্ট দোষ, সে বিষয়ে সংস্কৃত আলংকারিকরা বোধ হয় সকলেই একমত। বোধ হয় বলছি এই কারণে যে, অলংকারশাস্ত্রের সকল গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, কোনো আলংকারিক এ বিষয়ে বিপরীত মতাবলম্বী। চার্বাক যদি অলংকারশাস্ত্র লিখতেন তা হলে এ বিষয়ে অনেক পিলে-চমকানো মতের সাক্ষাৎ আমরা নিশ্চয়ই পেতুম। তবে আমার বিশ্বাস, অশ্লীলতা যে কাব্যদেহের শোভা বৃদ্ধি করে না, এ বিষয়ে আলংকারিকদের মতভেদ নেই।
আমি দু-একটি আলংকারিকের দু-চারটি কথা ধরে সেকালের বিদগ্ধমণ্ডলীর এ বিষয়ে রুচির পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, শ্লীলতাঅশ্লীলতা সুরুচির কথা, সুনীতির কথা নয়।
কাব্যের দোষগুণের একটি সহজবোধ্য ফর্দের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যাদর্শেই পাই। কাবাদর্শ পুরোনো গ্রন্থ, সুতরাং এ বিষয়ে প্রথমেই কাব্যাদর্শের কথা ধরা যাক। দণ্ডী বলেছেন–
কামং সর্বোহপালংকাররা রসমর্থে নিষিঞ্চতি,
তথাপ্যগ্রম্যতৈবৈনং ভারং বহতি ভূয়সা।
অর্থাৎ, যদিও সর্বপ্রকার অলংকার অর্থে রসসিঞ্চন করে, তবুও অগ্ৰাম্যতাই এ ভার বিশেষরূপে বহন করে। দণ্ডীর মতে অলংকারের সার্থকতা হচ্ছে কাব্যের অর্থের রস ফুটিয়ে তোলায়, কিন্তু অগ্ৰাম্য মনোভাব ও অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেই তা সুসাধ্য হয়। প্রেমচাদ তর্কবাগীশ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন–
সালংকারতয়া রসব্যঞ্জকোর্থে মধুর ইতি প্রতিপাদিতম্।
প্রাচীন আলংকারিকদের মতে –
বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।
অতএব দাঁড়াল এই যে, কাব্যের অর্থগত মাধুর্য অলংকারের সাহায্যে আরও মধুর হয়, যদি না কাব্যের শব্দ ও অর্থ গ্রাম্য তাদোষে দুষ্ট হয়।
৩.
আমরা অশ্লীল বলতে যা বুঝি, দণ্ডী গ্রাম্য বলতে তাই যে বুঝতেন তার প্রমাণ তার উদাহৃত কোনো কোনো শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই পাওয়া যায়। গ্রাম্য শব্দের অর্থ অবশ্য vulgar, তবে ইংরেজিতে যাকে indecent বলে তাকে vulgar বললে অত্যুক্তি হয় না।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অশ্লীলতা কাব্যের দোষ কেন। আলংকারিকদের মতে যা রসের প্রতিবন্ধক তাই দোষ, এবং যেহেতু অশ্লীলতা বিশেষরূপে রসের প্রতিবন্ধক, সে কারণ তা কাব্যের বিশেষ দোষ।
রসের স্থিতি বস্তুতে কি মানুষের মনে? কাব্যরস অলংকারের সংযোগে ফুটে ওঠে কি চেপে যায়, অশ্লীলতা রসের প্রতিবন্ধক কি সহায়ক? এসব দার্শনিক তর্ক এ স্থলে তোলবার প্রয়োজন নেই। কারণ, আলংকারিকদের বক্তব্য যে কি, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাদের মতে অশ্লীলতা-দোষ হচ্ছে কাব্যদেহের দোষ, অপর কোনো বস্তুর নয়। তাদের বিচার পোয়েটিসএর অন্তর্ভুত, এথিক্সএর নয়। সম্ভবতঃ এই কারণে হল প্রমুখ ইংরেজদের মতে যে কাব্য ঘোর অশ্লীল বলে গণ্য, সে কাব্য আলংকারিকদের কাছে সরস বলে মান্য হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাব্যবিচারের মার্গ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ইঙ্গমার্গ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকাশকার বলেছেন যে, কবির ভারতী–
নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
যাঁদের মতে কবির প্রতিভা নিয়তিকৃত নিয়মের অধীন নয়, তারা যে কবি প্রতিভাকে মানুষের হাতগদ্য সামাজিক বিধিনিষেধের অধীন ব’লে স্বীকার করবেন না সে কথা বলাই বাহুল্য। সেকালে কাব্য নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত, সত্য অথবা শিবের হাত ধ’রে নয়।
৪
গ্রাম্যতা অবশ্য শব্দেরও দোষ, অর্থেরও দোষ। একালের মত সেকালেও ভাষা, সাধুভাষা ও ইতরভাষা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সংস্কৃত ভাষার সাধু শব্দের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় আছে, ইতর শব্দের সঙ্গে নেই বললেই হয়। সুতরাং শব্দের গুণ-দোষ বিচার না করে আলংকারিকদের মতে শব্দের অর্থগত গ্ৰাম্যতার পরিচয় নেওয়া যাক। সেকালে গ্রাম্যতার অর্থ একালের চেয়ে ঢের ব্যাপক ছিল। দণ্ডীর মতে—
কন্যে কাময়মানং মাং ন ত্বং কাময়সে কথম্।
উক্তিটি অর্থের গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট। অপর পক্ষে–
কামং কন্দর্পচাণ্ডালো ময়ি বানাক্ষি নির্দয়ঃ।
এই উক্তিটি শুধু ‘অগ্রাম্যোহর্থ’ নয়, উপরন্তু রসাবহ।
এ উভয়ের ভিতর প্রভেদ কোথায়, তা ধরতে একটু চেষ্টা করা যাক। কেননা বিনা চেষ্টায় তা ধরা শক্ত। এক বিষয়ে এ দুয়ের ভিতর একটা মস্ত মিল আছে। এ দুটি উক্তিই সমান কবিত্ব-ছুই। তার পর দুটিতেই একই মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে; দুয়ের ভিতর প্রভেদ মাত্র এই যে, প্রথমটি স্পষ্ট কথায় বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এর থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীনদের মতে কথা সোজাসুজিভাবে বললে তা গ্রাম্যত-দোষে দুষ্ট হয়, আর বেঁকিয়ে চুরিয়ে বললেই তা শুধু অগ্ৰাম্য নয়, রসাবহ হয়। অর্থাৎ বুক ও মুখের ভিতর কর্ড লাইনই গ্রাম্য এবং লূপ অগ্ৰাম্য। যেমন বিভিন্ন লোকের রুচি বিভিন্ন, তেমনি বিভিন্ন কালের রুচি বিভিন্ন। একালে অনেকে। হয়তো উক্ত প্রথম পদটিই বেশি পছন্দ করবেন; কারণ, তার ভিতর আর কিছু না থাক স্পষ্ট passion আছে, আর শেষ পদটির ভিতর যা আছে, সে শুধু সেকালের সাহিত্যিক fashion মাত্র। সে যাই হোক, সেকালের সমালোচকদের দল কি বলা হল তাতে বিচলিত হতেন না, কি করে বলা হল তাই ছিল তাদের কাছে বড় জিনিস। একালের ভাষায়, contentএর চাইতে formকে তারা বেশি মর্যাদা দিতেন। বিশেষ করে এ দুটি উদাহরণের উল্লেখ করলুম এই জন্যে যে, দণ্ডী না বলে দিলে এর কোটি গ্রাম্য ও কোটি অগ্ৰাম্য, তা আমরা চট করে ধরতে পারতুম না।
৫.
কালক্রমে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বাক্যের পৃথক পৃথক্ দোষ বলে গণ্য হয়। দণ্ডীর পরবর্তী আলংকারিক বামন এই উভয়বিধ দোষের উল্লেখ করেছেন। বামনের পরবর্তী আলংকারিকরা তার মতই অনুসরণ করেছেন।
এখন দেখা যাক এ দুই দোষের মূলে কি আছে। বামন বলেন–
লোকমাত্রপ্রযুক্তং গ্রাম্যম্।
অর্থাৎ যে কথা শুধু জনসাধারণের মুখে শোনা যায় কিন্তু শাস্ত্রে যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, সেই কথাই গ্ৰাম্য। এ কথা শুনে মনে হয় যে, তারা লোকভাষা ও শাস্ত্রীয় ভাষাকে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা বলে গণ্য করতেন; অর্থাৎ লেখায় মুখের কথা চলবে না, আর মুখে বইয়ের কথার স্থান নেই। সংক্ষেপে, সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে মৌখিক ভাষার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। এ রকমের মত একালের অনেক বঙ্গ-আলংকারিক ব্যক্ত করেন। সংস্কৃত আলংকারিকরা অবশ্য এ মতের সমর্থন করেন না। তাদের মতে গ্রাম্য পদের ন্যায় অপ্রতীত’ পদ কাব্যে অব্যবহার্য। অতীত শব্দের অর্থ কি?–
শাস্ত্রমাত্রপ্রযুক্তমপ্রতীতম্
অর্থাৎ
শাস্ত্র এব প্রযুক্তং যন্ন লোকে, তদপ্ৰতীতং পদম্
অর্থাৎ পণ্ডিতি শব্দ ও গ্রাম্য শব্দ দুই কবির কাছে সমান অস্পৃশ্য। এ বিষয়ে আমাদের দেশের অলংকারিকদের সঙ্গে ফরাসিদেশের ক্ল্যাসিকাল অলংকারিকদের মতের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। তারাও সাহিত্যরাজ্য থেকে pedantic ও ভাঙ্গার শব্দসকল বহিস্কৃত করে দেবার জন্য ধনুক ধারণ করেছিলেন। আমরাও যখন চলতি ভাষার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করি, তখন আমরাও সে ভাষাকে ইতর ভাষার কোঠাতে ফেলে দিই; যদিচ চলতি কথার সঙ্গে ইতর কথার প্রভেদ যে কি, তা সকলেই জানেন। আর যিনি তা না জানেন, তাঁর পক্ষে নীরব থাকাই শ্রেয়।
৬.
এর থেকে বোঝা গেল, বামন প্রমুখ আলংকারিকদের মতে গ্রাম্যতা হচ্ছে শুধু শব্দের দোষ। বামন এই সূত্রে যে উদাহরণ দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, বাক্য অশ্লীল না হয়েও গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হতে পারে–
কষ্টং কথং রোদিতি ফুৎকৃতেয়ম।
এ উক্তিতে অশ্লীলতার নামগন্ধও নেই, কিন্তু ‘ফুৎকৃতি’ শব্দই রোদনের রসভঙ্গ করেছে। অবশ্য বাংলা ভাষায় ফুৎকার ইতর শব্দ নয়, তবুও ফোঁ ফোঁ করে কাঁদছে কথাটা আমাদের কানে করুণরসাবহ নয়।
অপর পক্ষে অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেও যথেষ্ট অশ্লীল বাক্য রচনা করা যায়। সুতরাং অশ্লীলতা-দোষ কাকে বলে, তা আলংকারিকদের মুখে শোনা যাক। বামন বলেছেন যে, সেই বাক্য অশ্লীল যা–
ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী
অর্থাৎ যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। এই হচ্ছে এ বিষয়ে অলংকারশাস্ত্রের শেষ কথা। কারণ কাব্যপ্রকাশ সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি নামজাদা, অলংকারশাস্ত্রের অর্বাচীন গ্রন্থসকলে ঐ বামনের উক্তিই পুনরুক্ত হয়েছে, এবং, আমার বিশ্বাস, এই কথাই এ বিষয়ে চরম কথা। অমঙ্গলের আশঙ্কার কথা ছেড়ে দিলে যাতে লোকের মনে লজ্জা কিংবা জুগুপ্সার জন্ম দেয় তাই হচ্ছে অশ্লীল বাক্য। এখন জিজ্ঞাস্য, কার মনে? আলংকারিকদের মতে, সামাজিকদের মনে। তারা সামাজিক বলতে বুঝতেন সেই সম্প্রদায়ের লোক যারা যুগপৎ সভ্য ও সহৃদয়, এক কথায় কাচাৰ্ড সোসাইটি। দেশভেদে ও যুগভেদে কাচাৰ্ড সোসাইটিরও রুচি বিভিন্ন। আনাতোল ফ্রাঁসের কথা ইংরেজের রুচিতে অশ্লীল ঠেকে, ফরাসিদের রুচিতে নয়। আলংকারিকরা অবশ্য স্বদেশি সামাজিকদের কথা বলেছেন, বিদেশি সামাজিকদের নয়।
৭.
শ্লীলতা-অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলংকারিকদের সেকেলে মতামত একালের লোককে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্য কি? আমাদের দেহে এখন তো আর সেকালের মন নেই। যুগে যুগে লোকের মনের পরিবর্তন ঘটে, সুতরাং সেকালের বিধিনিষেধের একালে সার্থকতা নেই। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। মানুষের মতামত যে পরিমাণে বদলায়, তার মনের প্রকৃতি সে পরিমাণে বদলায় না। অতএব অনেক সেকেলে মতামতের অন্তরে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় সে মনোভাব কস্মিনকালেও একেবারে বাতিল হয়ে যায় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা আবিষ্কার করি যে, প্রাচীন মন বর্তমান মনের চাইতে এক ধাপ উঁচুতে উঠেছিল। আমার বন্ধু শ্ৰীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর রচিত কাব্যজিজ্ঞাসায় প্রমাণ করেছেন যে, যে সমাজের মনে কাব্যজিজ্ঞাসা নেই সে সমাজ কখননা। কাব্যমীমাংসায় উপনীত হতে পারে না। এই কারণেই আমাদের কাব্যবিচার প্রায়ই বাজে ও এড়ো হয়। অলংকারিকদের কাব্যবিচারের আর যাই ত্রুটি থাক্ সে বিচার কখনো ভুল পথে যায় নি; বেশি দূর যেতে না পারে, কিন্তু ঠিক পথেই গিয়েছে।
সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন কথার আবির্ভাব হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে ‘সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা। এখন, এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সাহিত্যের স্বাস্থ্য নিয়ে কখনো মাথা ঘামান নি; তারা যার আলোচনা করেছেন, সে হচ্ছে কাব্যের রূপ। আর, যার রূপ নেই, তা যে কাব্য নয়, এ কথা অবিসম্বাদী। এই রূপের বিচার করাই সমালোচকের একমাত্র কর্তব্য।
৮.
আলংকারিকদের মতে অশ্লীলতা একটি দোষ; কেননা, তা কাব্যের রূপ নষ্ট করে। কারণ, ব্ৰীড় জুগুপ্সা প্রভৃতি মনোভাব কাব্যের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়, একটি বদ সুর লাগালে যেমন রাগের রূপ নষ্ট হয়; কারণ, শ্রোতার কানে তা বেসুরা লাগে।
এ কথা বলা বাহুল্য যে, বেসুর তার কানেই শুধু ধরা পড়ে যার কানে ও প্রাণে সুর আছে। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ, কেননা তা সামাজিক লোকের রুচিতে বেখাপ্পা ঠেকে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক বলতে আলংকারিকরা বুঝতেন কাব্যরসিক। মানুষের ভিতর কাব্যরসিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সংগীতরসিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। এ জাতিভেদ ডিমোেক্রাসিও দূর করতে পারবে না। আলংকারিকদের মতে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাব্যরসিকসমাজের রুচি।
এখন, সকল সমাজের লোক সমান কাব্যরসিক নয়। দার্শনিক হিসাবে জর্মানদের যেমন খ্যাতি আছে, নৈতিক হিসাবে ইংরেজদের, কাব্যরসিক হিসাবে ফরাসিদের তেমনই খ্যাতি আছে। ফরাসিদের সুরুচি সম্বন্ধে কাইজারলিঙের মত অবাধে গ্রাহ্য করা যেতে পারে, কারণ তিনি একাধারে ঘোর দার্শনিক ও পুরো জর্মান। তার কথা এই–
The French taste is in itself so good that the on of Paris-that impersonal anonymous they-has a surer judgment than any save the most unusual individual. (Europe)
অথচ ফরাসি রুচি ইংরেজি রুচির সঙ্গে মেলে না। সুতরাং আমাদের পূর্বপুরুষদের অশ্লীলতা সম্বন্ধে ধারণা ইংরেজদের ধারণার সঙ্গে মেলে না বলে যে তা নিকৃষ্ট, এমন কথা মূখ ছাড়া আর কেউই বলবেন না। কাব্য সম্বন্ধে সুরুচি ও কুরুচি লোকের কাব্যজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে, কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নৈতিক কিংবা সামাজিক মতামতের উপর নির্ভর করে না। এই সত্যটিই আলংকারিকরা বহু পূর্বে আবিষ্কার করেছিলেন।
৯.
সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা বাক্যটি সম্পূর্ণ নিরর্থক। সাহিত্যের স্বাস্থ্য জিনিসটি কি এবং কোন্ কোন্ বস্তুর সদ্ভাবের উপর তা নির্ভর করে, তার নির্ভুল হিসাব আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পেরেছেন বলে আমি জানি নে। আর যদিই ধরে নেওয়া যায়, সাহিত্যেরও স্বাস্থ্য বলে একটা গুণ আছে, তাহলে সে স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন কে এবং কি উপায়ে? পুলিশ ও সমালোচক সাহিত্যের উপর কড়া শাসনের বলে? বলা বাহুল্য, যারা এরূপ শাসনের পক্ষপাতী, তারা স্বাস্থ্যের বিষয় সব জানতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের বিষয় কিছুই জানেন না।
আমার মনে হয়, যাঁরা মুখে বলেন সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা, তাঁরা আসলে চান সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা। আর তাদের কাছে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার অর্থ সমাজ রক্ষা। সমাজ সুস্থই হোক আর অসুস্থই হোক তা যেমন আছে সেই ভাবেই টিকে থাক্, এই হচ্ছে তাদের আন্তরিক কামনা; এবং এ-জাতীয় লোক কথাকে অত্যন্ত ডরান, কারণ তাদের ধারণা সামাজিক মনের উপর কথার প্রভাব মারাত্মক, বিশেষতঃ সে কথা যদি উজ্জ্বল ও মনোহারী হয়। পলিটিশিয়ানরা যখন সমাজের উপরে খড়্গহস্ত হন, তখন এই দল বিশেষ বিচলিত হন না; কারণ তারা জানেন, ও হচ্ছে কাজের কথা। কবির উক্তিই তাদের কাছে অসহ্য, কেননা এ হচ্ছে ভাবের কথা। আর ভাবের স্পর্শেই মানুষের মনোভাব বদলে দিতে পারে, তেল-নুন-লকড়ির কথাতে পারে না; কারণ সে কথা মানুষের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে বাক্য সামাজিক লোকদের মনে এই জাতীয় অশঙ্কার উদ্রেক করে, সে বাক্য রসের প্রতিবন্ধক কি না।
১০.
সংস্কৃত আলংকারিকরা ইংরেজিতে যাকে বলে মর্যালিটি তার বিশেষ বিচার করেন নি। তবুও এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে উক্তি মানুষের মরাল সেক্সকে পীড়িত করে, তাও ছিল তাদের মতে কাব্যে বর্জনীয়। কবি রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় বলেছেন–
অসদুপদেশকত্বাত্তর্হি নোপদেষ্টব্যং কাব্য ইত্যপরে।
অর্থাৎ অপর আলংকারিকদের মতে কাব্যে অসদুপদেশ দেওয়া অকর্তব্য। কিন্তু তাঁর মতে–
অস্ত্যয়মুপদেশঃ কিন্তু নিষেধ্যত্বেন ন বিধেয়ত্বন।
অর্থাৎ অসাধুপদেশেরও কাব্যে স্থান আছে, কিন্তু নিষেধ হিসাবে বিধি হিসাবে নয়। রাজশেখরের সঙ্গে অপর আলংকারিকদের মতের প্রভেদ কোথায়, বোঝা কঠিন। বোধ হয় অপর আলংকারিকদের মতে অসদুপদেশ কাব্যে একেবারে বর্জনীয়, কিন্তু রাজশেখরের মতে কাব্যে সে উপদেশ থাকতে পারে, কবি যদি সে উপদেশকে অসৎ বলেই উল্লেখ করেন। কাব্যের প্রভাব যে লোকের মনের উপর প্রবল, সে ধারণা তাদেরও ছিল। রাজশেখর বলেছেন–
কবিবচনায়ত্তা লোকযাত্রা। সা চ নিঃশ্রেয়সমূলম্।
এর বাংলা : লোকের জীবনযাত্রা কবিবচনের আয়ত্ত এবং সে জীবনযাত্রার মূল হচ্ছে নিঃশ্রেয়স, ইংরেজিতে যাকে বলে virtue, welfare। যারা বিশ্বাস করতেন যে, মর্যালিটি হচ্ছে জীবনযাত্রার মূল, তাঁদের মতে কাব্যের ফুল সে মূল হতে বিচ্ছিন্ন নয় এবং সে মূলের সংস্কার কাব্যকুসুমের অন্তর্নিহিত। এর থেকে দেখা যায় অশ্লীলতার ন্যায় অসদুপদেশও সেকালেও কাব্যের দোষ বলেই গণ্য ছিল। তবে আমাদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ এই মাত্র যে, তারা অসৎ বাক্যকে এসথেটিক ইমোশনের প্রতিবন্ধক হিসেবে দুষ্ট মনে করতেন, অপর পক্ষে আমরা আমাদের সোনার সংসার ছারখারে যাবে, এই ভয়েই অস্থির। এ প্রভেদ মস্ত প্রভেদ। কাব্যমীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন beautyর অনুরক্ত, আমরা হয়েছি utilityর ভক্ত।
১১
আমরা যে এসথেটিক ইমোশনকে আমল দিই নে, তার কারণ আমরা ইংরেজিশিক্ষিত। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে এ রসে বঞ্চিত, এ কথা সবাদিসম্মত। আমি পূর্বে বলেছি, ইংরেজ জাতি ঘোর নৈতিক বলে গণ্য, তবে মর্যালিটিকে তারা ইউটিলিটিতে পরিণত করেছে। আমরা ইংরেজের শিষ্য, ফলে আমাদের সুন্দর-অসুন্দর সৎ-অসৎ সত্যমিথ্যার জ্ঞান, ইংরেজি জ্ঞানের অনুরূপ। কাব্যজিজ্ঞাসা ও ধর্মজিজ্ঞাসার প্রভেদ আমরা ধরতে পারি নে। আমাদের কাব্যে সুরুচি ইংরেজি অরুচির তর্জমা মাত্র। আমি এ প্রবন্ধ শুরু করেছি হল সাহেবের সংস্কৃত কাব্যে অরুচির উল্লেখ করে। আর শেষ করছি এই বিংশ শতাব্দীর একটি ইংরেজ ওরিয়েন্টালিস্টের কথা দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর এ বিষয়ে মতামত বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ বিদষ্মমণ্ডলীর কাছে একেবারেই অগ্রাহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মন উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি মতের দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করে নি। এখন বাসবদত্তা সম্বন্ধে কীথের কথা শোনা যাক—
It would be quite unjust to accuse Subandhu of indecency or savagery as one distinguished editor did. To apply mid-Victorian conceptions of propriety to India is obviously absurd and wholly misleading. Indian writers, not excluding Kalidasa, indulge habitually con amore in minute descriptions of the beauty of women and the delights of love which are not in accord with western conventions of taste. But the same condemnation was applied by contemporaries to Swinburne und Shakespeare’s frankness is more resented by Tinglish than by German taste. What is essential is to repel the councction of such description nith iinmorality and to assert that they must be approved or condemned on artistic grounds alone. There is all the world of difference between that we find in the great poets of India and the frank delight of Vartial and Pertronius in descriptions of immoral scenes. (History of Sanskrit Literature)
সেকালের আলংকারিকরা যদি একালে সশরীরে উপস্থিত থাকতেন এবং ইংরেজি ভাষা জানতেন, তাহলে কীথ সাহেবের কথায় তারা সম্পূর্ণ সায় দিতেন, বিশেষতঃ তার বক্ষ্যমাণ উক্তিটি তাদের কাছে ষোলো আনা গ্রাহ্য হত। কীথ সাহেব বলেছেন যে–
What is essential is to assert that they must be approved or condemned on artistic grounds.
বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মতের সঙ্গে যে হিন্দু যুগের ভারতবর্ষীয় মতের ঐক্য থাকবে, এটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। মানুষ এককালে যে-সত্যের সন্ধান পায়, তা চিরকালের সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তা অজ্ঞতার আবরণে ঢাকা পড়ে, আবার কালক্রমে সে আবরণ মুক্ত হয়; তখন লোকে মনে ভাবে যে, সেটি নূতন-আবিষ্কৃত সত্য।
আমি এ প্রবন্ধে কাব্যে অশ্লীলতা নামক দোষ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করলুম এই কারণে যে, সে মত প্রাচীন হলেও অনবীন নয়।
১৩৩৬ বৈশাখ
চিত্রাঙ্গদা
প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিষদে পঠিত
রবীন্দ্রপরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীমান সোমনাথ মৈত্র আমাকে আপনাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সম্বন্ধে দু চার কথা বলবার জন্য বহুবার অনুরোধ করেছেন। তার অনুরোধ রক্ষা করতে আমি সদাই প্রস্তুত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি বরাবরই ইতস্ততঃ করেছি। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমালোচনা করতে আমি ভয় পাই।
এ বিষয়ে যখনই কিছু বলবার প্রবৃত্তি মনে জেগে ওঠে, তখনই এ প্রশ্নও আমার মনে উদয় হয় যে, কাব্য সমালোচনা করবার সার্থকতা কি? আমি জানি যে, সমালোচনা জিনিসটে সাহিত্য-জগতের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। বরং আমাদের স্কুলকলেজে কবির চাইতে সমালোচকেরই প্রাধান্য বেশি। প্রসিদ্ধ ফরাসি দার্শনিক তেই-এর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস আমরা অনেকেই পড়েছি। কেননা ইংরেজি সাহিত্যের এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য সে বই আমরা অধ্যয়ন করতে ও যথাসাধ্য কণ্ঠস্থ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু উক্ত বিপুল সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাংপরিচয় আমাদের ক’জনের আছে? এ ক্ষেত্রে সমালোচনা কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষে একটি অন্তরায় মাত্র। কোনো বিশেষ ভাষার সমগ্র কাব্যের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিলেও একটি বিশেষ কবির কাব্যের রসম্বাদ করবার পক্ষেও তার উক্তরূপ সমালোচনা তেমন অনুকূল নয়। গেরফিনুস Gervinus অথবা Dowden ডাউডেনের সমালোচনা পড়ে ক’জন পাঠক শেক্সপীয়ারের কাব্যের রসগ্রাহী হয়েছেন। আমরা যখন ইেন পড়ি অথবা গেরফিনুস পড়ি, তখন আসলে সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে তাঁদের ফিলসফিই পড়ি। এ জাতীয় ঐতিহাসিক দার্শনিক সমালোচনার গলদ এই যে, কাব্যের আত্ম দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, আর কাব্যরসিক মাত্রই জানে যে, কাব্য হচ্ছে ফিলসফির বহিভূত, কারণ মানবাত্মার যে মূর্তির সাক্ষাৎ কাব্যে পাওয়া যায়, তার সাক্ষাৎ দর্শনে মেলে না।
২.
আমার কথা ভুল বুঝবেন না। আমি এ কথা বলতে চাই নে যে, কবি ফিলসফার হতে পারে না, আর ফিলসফার কবি হতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কবিও আছেন যাকে লোকে মহাদার্শনিক মনে করে, অপরপক্ষে এমন দার্শনিক আছেন যাকে লোকে মহাকবি মনে করে। প্লেটোর দর্শন তো কাব্য বলে ইউরোপে বহুকাল থেকে গণ্য হয়েছে। এমন কি স্পিনোজার এথিক্স, জিয়োমেটির পদ্ধতিতে লেখা হলেও তা অনেকের কাছে একখানি মহাকাব্য। অপর পক্ষে শেলি সেক্সপীয়ারের ফিলসফি নিয়ে ইংলণ্ডে কত-না আলোচনা হয়েছে। এমন কি ফিলসফি অব রবীন্দ্রনাথ নামক একখানি গ্রন্থ আছে। অপর পক্ষে উপনিষদ্, কাব্য কি দর্শন, তা মনীষিবৃন্দ আজও ঠিক করতে পারেন নি। কবির সঙ্গে দার্শনিকের প্রভেদ কোথায়, intuitionএর সঙ্গে conceptএর প্রভেদ কি সে তর্ক আজ তুলতেই চাই নে, কেননা সে আলোচনা হবে আগাগোড়া দার্শনিক, অতএব অপ্রাসঙ্গিক। উপরন্তু আমার পক্ষে সে চর্চা নিতান্তই অনধিকারচর্চা।
আমি শুধু এই সত্যটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কাব্যসমালোচক মাত্রেই কতক অংশে ফিলসফার হতে বাধ্য। আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখাবিশেষ। গ্রীসে অ্যারিস্টটল যে শ্রেণীর লোক ছিলেন, এ দেশে অভিনব গুপ্তও সেই শ্রেণীর লোক। উভয়েই নৈয়ায়িক।
আগে একটা দার্শনিক মত খাড়া করে তার পর সেই মতানুসারে কাব্যের হীনতা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা যে বৃথা, সে জ্ঞান আজকের লোকের হয়েছে। তাতেই ফরাসি দেশের নবযুগের সমালোচকরা নিজেদের ইমপ্রেশনিস্ট বলে পরিচয় দেন, অর্থাৎ তাদের মতে কাব্যবস্তু হচ্ছে সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা এ আশাও করেন যে, তাঁদের মতামতের universal validity আছে। কোনো সমালোচকের পক্ষে এ আশা ত্যাগ করা অসম্ভব। কারণ আমি যখনই কোনো মতকে সত্য বলে মনে করি, তখনই মনে করি যে, তা সকলের পক্ষে সত্য। তেমনই, যখনই বলি এ বস্তু সুন্দর তখনই এ কথাটা উহ্য রয়ে যায় যে, তা সকলের কাছেই সুন্দর। ইউনিভার্সাল ভ্যালিডিটি অবশ্য দর্শনের বিষয়। সুতরাং আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যতই অদার্শনিক কথা বলি-না কেন, একটা-না-একটা ফিলসফি তার মধ্যে থেকে উকি মারবে। আর সে ফিলসফি যে কত কঁচা অথবা পচা, তা ধরা পড়বে আপনাদের দার্শনিকচূড়ামণি প্রেসিডেন্টের কাছে। অথচ কি করা যায়? কাব্য ম্যাজিক হতে পারে, কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।
আর-এক জাতীয় সমালোচনা আছে যার রিজুনএর সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই, যা ষোলো আনা আরিজনএর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কাব্যবিশেষের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করা। প্রায়ই দেখা যায়, এ নিন্দা-প্রশংসার মূল হচ্ছে রাগ-দ্বেষ। কোনো কারণে কবি নামক মানুষটির উপর বিরক্ত হলে সমালোচক তাঁর কাব্যের নিন্দা করেন এবং অনুরক্ত হলে প্রশংসা করেন। এ অনুরাগ-বিরাগ কাব্যজগতের কথা নয়। আমাদের এই চিরদিনের সমাজ-সংসারের কথা। এ রকম সমালোচনার জন্মস্থান হচ্ছে হৃদয়। আলংকারিকরা যে হৃদয়ের কথা বলেন এ সে হৃদয় নয়, রক্তমাংসে-গড়া সেই হৃদয়, যা প্রাণী মাত্রেরই বুকের ভিতর দিবারাত্র ধড়ফড় করছে। সুখের বিষয়, এই মাংসপিণ্ড হতে আমি কোনোরূপ মতামত উদ্ধার করতে পারি নে। তা যে পারি নে তার প্রমাণ, সাহিত্যিক হিসাবে কেউ কেউ আমার সুখ্যাতি করেন, কেউ কেউ বা অখ্যাতি। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে, আমার অন্তরে হৃদয় বলে পদার্থটি নেই। আপচ্ছান্তি।
এতদ্ব্যতীত আর-এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যারা কাব্যের বিচারক। এই সব কাব্যজগতের ধর্মাধিকরণের দল, কোন্ কবি কাব্যের কোন্ বিধি পালন করেছেন ও কোন্ নিষেধ অমান্য করেছেন, সেই অনুসারেই কাব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেন। আমি কাব্যের এরূপ বিচারক হতে পারি নে, কারণ কাব্যজগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলীর অস্তিত্ব আমি মানি নে। কাব্যেরও অবশ্য law আছে, কিন্তু প্রতি যথার্থ কবিই হচ্ছেন তার rules এর স্রষ্টা। যে নিয়মের সাক্ষাৎ কালিদাসের নাটকে দেখতে পাই সে নিয়মাবলীর সাহায্যে শেক্সপীয়ারের কাব্যজগতে সৃষ্টির মূল পদ্ধতি যে তাই সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আপনারা আমাকে রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর জজিয়তি করবার জন্য আহ্বান করেন নি, কারণ সে কাজের ভার তো মাসিক সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রেরাই অযাচিত ভাবেই নিয়েছে।
৪.
রবীন্দ্র পরিষদের প্রস্তাবে সম্মত হবার পূর্বে আমার ইতস্ততের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমাকে বক্তৃতা করতে হবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। আমাকে কি এ ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ একজন কবি? জগবিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে কাব্যসমালোচকদের বিজ্ৰপ করে বলেছেন, পৃথিবীতে, কোনো দেশে কোনো কালে মানবজাতি কি তোমাদের সার্টিফিকেটের উপর আস্থা রেখে কাউকে কবি বলে স্বীকার করেছে, না, লোকমতে যারা কবি বলে গণ্য ও মান্য হয়েছে, তাঁদের সম্বন্ধেই তোমরা মুখর হয়ে উঠেছ? ইতালিতে দান্তে ও বিলাতে শেক্সপীয়ার লোকমতে বড় কবি বলে গণ্য হবার পরেই না তোমরা। তাঁদের বিষয়ে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেছ? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে, হাঁ, তাই। এ কথা যে সত্য তার প্রমাণের জন্য সাগর লঙ্ঘন করবার প্রয়োজন নেই। রামায়ণ ও মহাভারত যে মহাকাব্য সে বিষয়ে লোকমত সমালোচকের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি।
এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে, কবিবিশেষ যে কবি, এই কথাটা মেনে নিয়েই তাঁর কাব্যের আমরা আলোচনা করতে পারি। কারণ কবিত্বশক্তি বস্তু যে কি, তা লজিকের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। তা যে যায় না তা মানুষ বহুকাল পূর্বে বুঝতে পেরেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিক বামনাচার্য বলেছেন যে, ‘কবিত্ববীজং প্রতিভান, এবং উক্ত সূত্রের তিনি বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করেছেন–
কবিত্বস্য বীজং কবিত্ববীজং, জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষঃ।
এ ব্যাখ্যা কি খুব পরিষ্কার? ‘জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষ’ বলায় শুধু বলা হয় যে, কবিত্বশক্তি অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ মিষ্টিরিয়। আমরা অপরের প্রতিভা থাকলে তা চিনতে পারি, কিন্তু তা যে কি স্পষ্ট করে বলতে পারি নে। এর কারণ প্রতিভা স্বপ্রকাশ। কিন্তু তা প্রকাশ করে বলবার প্রয়াস বৃথা। এই চেষ্টা যে ব্যর্থ তার প্রমাণ অ্যারিস্টটল থেকে হেগেল পর্যন্ত সকল দার্শনিকই দিয়েছেন। প্রতিভার সন্ধান যে সাইকলজি নামক বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায় না তার প্রমাণ, ও-বস্তুর মূল কারণ একালের বৈজ্ঞানিকরা ফিজিঅলজির অন্তরে খুঁজেছেন। প্রতিভা যে একরকম insanity এ মতও ইউরোপে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। সে মত সত্য কি মিথ্যা সে কথা আমি বলতে পারি নে। আমার বক্তব্য এই যে, প্রতিভা যদি একরকম ইন্স্যানিটি হয় তা হলে এ জাতীয় ইনস্যানিটি অনেকেই বরণ করে নেবেন, অন্ততঃ আমি তো নেই। এই প্রতিভার স্পষ্ট কার্য হচ্ছে আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত ও আলোকিত করা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্পর্শে যাদের মন আলোকিত হয়ে ওঠে তার। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নিজেই realise করেছেন, আর সে আলোক যাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি লজিকের সাহায্যে তাঁদের অন্তরের রুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিতে আমি পারব না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ও মহাকবি এই কথাটি মেনে নিয়েই তার একটি বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।
৫
কোনো কবিকে বড় কবি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার জিজ্ঞাসা আমাদের মনে উদয় হয়। এ ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হচ্ছে, কাব্যের প্রয়োজন কি? প্রশ্ন বহু পুরাতন। আমাদের দেশে প্রাচীন আলংকারিকরা এ প্রশ্নের যা হোক একটা-না-একটা উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি তাদের দু-একটা মতের উল্লেখ করব। এ স্থলে বলে রাখা আবশ্যক যে, আমি ফাঁক পেলেই যে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামত পাঁচজনকে ফুর্তি করে শোনাই, তার কারণ এ নয় যে, আমি তাদের কথা এ বিষয়ে চুড়ান্ত বলে বিশ্বাস করি কিংবা তাদের মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করি। আলংকারিক হিসাবে অ্যারিস্টটল বড় কিংবা দণ্ডী বড়, হেগেল বড় কিংবা বিশ্বনাথ বড়, সে বিচার করবার শক্তিও আমার নেই, প্রবৃত্তিও আমার নেই। আমি যে সংস্কৃত অলংকারিকদের দোহাই দিই তার একমাত্র কারণ আমি বাংলা ভাষায় কথা কই, আর সংস্কৃত কথা বাংলা ভাষার মধ্যে যত সহজে বেমালুম খাপ খায়, গ্রীক ও জর্মান কথা ততই সহজে সমালুম বেখাপ্পা হয়।
এখন প্রস্তুত বিষয়ে ফিরে আসা যাক। বামনাচার্য বলেছেন–
কাব্যং সদৃষ্টাদৃষ্টাৰ্থ প্রীতিকীর্তিহেতুত্বাৎ।
বামন নিজেই উক্ত সূত্রের বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যা করেছেন–
কাব্যং সচ্চারু দৃষ্টপ্রয়োজনম্ প্রীতিহেতুত্বাৎ।
অদৃষ্টপ্রয়োজনম্ কীর্তিহেতুত্বাৎ।
সংস্কৃত শাস্ত্রকারের এত সাঁটে কথা কন যে, আমাদের পক্ষে তাদের রচিত সূত্র যেমন সহজবোধ্য তার ব্যাখ্যাও প্রায় তদ্রুপ। আমি অনুমান করছি যে, বামনাচার্যের কাব্যের দৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যভোক্তার প্রীতি, আর তার অদৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যকর্তার কীর্তি। এখন এই অদৃষ্টপ্রয়োজনের কথা মুলতবি রেখে দৃষ্টপ্রয়োজনের কথাটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক, কারণ আজকের সভায় যারা একত্র হয়েছি তাদের কেউই কাব্যের কর্তা নন, সবাই ভোক্তা। কর্তা যে আমরা নই তার প্রমাণ, কবিকীর্তি আমরা কেউই লাভ করি নি, যদিচ আমরা কেউ কেউ পদ্য লিখেছি।
৬.
কাব্যরস আস্বাদ করে যে আমরা প্রীতি লাভ করি এ তো প্রত্যক্ষ সত্য, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর তর্ক নেই। কেননা, যা দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ তা স্বতঃসিদ্ধ। তবে মনে রাখবেন, যে বিষয়ে তর্ক নেই সেই বিষয়েই মানুষের তর্কের শেষ নেই। তাই এই প্রীতিকথা নিয়ে দেদার তর্ক করা যেতে পারে, কেননা যুগ-যুগ ধরে করা হয়েছে। প্রীতি অর্থ যদি হয় pleasure, তাহলেই বামনাচার্যের মতকে hedonismএর কোঠায় ফেলে দেওয়া যায়। কাব্য সম্বন্ধে ও-মত অগ্রাহ্য, কেননা। ও-মতানুসারে কাব্য বিলাসের একটি উপকরণ হয়ে পড়ে, অর্থাৎ মাল্যচন্দনবনিতার দলে পড়ে যায়। এ তর্ক ইউরোপীয় পণ্ডিতরা দেদার করেছেন। বোধ হয় তাদের সমধর্মী পণ্ডিতের দল এ দেশে সেকালেও ছিলেন। সে কারণ নব্য আলংকারিকরা প্রীতির বদলে ‘আনন্দ’ শব্দের উপরেই ঝোক দিয়েছেন। এমন কি নব্য আলংকারিকদের আদিগুরুর নাম আনন্দবর্ধনাচার্য। এ আনন্দ যে কোনো লৌকিক আনন্দ নয় সে কথা নব্য আলংকারিকরা স্পষ্টাক্ষরে লিখে গেছেন। আনন্দের ইংরেজি pleasure নয়, joy। A thing of beauty is a joy for ever—কবি কীটসের এ বাণী তারা বিনাবাক্যে শিরোধার্য করে নিতেন, কারণ নিরানন্দ হওয়াটাই সংসারের দাসত্বের ফল, আর আনন্দই মুক্তি। প্রীতি দৃষ্টপ্রয়োজন এ কথা বলার অর্থ কাব্যামৃত-রসাস্বাদ করার আনন্দ ব্যতীত কাব্যের অপর কোনো দৃষ্টপ্রয়োজন নেই। মানবমনের প্রীতিসাধনই কাব্যের একমাত্র utility।
এ কথা প্রসন্নমনে মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষে পুরাকালেও কঠিন ছিল, আর একালে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ একালে মানুষের রক্তমাংসের যা প্রয়োজন তাই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন বলে গণ্য হয়েছে এবং সেই প্রয়োজনের কায়মনোবাক্যে সাধনা করাই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং কাব্যের সার্থকতা আমরা মানুষের সাংসারিক প্রয়োজনের মাপকাঠিতে যাচাই করতে সদাই প্রস্তুত।
৭.
কাব্যামৃতরসের আস্বাদ যে মুক্তির আস্বাদ এ মতে সায় দেওয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে অতি সহজ ছিল, কেননা তাদের মতে জীবনটা হচ্ছে নিছক ভবযন্ত্রণা। জীবনের ধর্ম হচ্ছে আত্মাকে তার দাস করা, আর মনের এই দাসত্ব হতে মুক্তির প্রসাদেই মানবাত্মা আনন্দ লাভ করে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, সকল দেশেই সকল যুগেই অলংকারশাস্ত্র হচ্ছে দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখা মাত্র। সুতরাং আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্রের মুক্তির সঙ্গে কাব্যচর্চার মুক্তির জ্ঞাতিত্ব আছে ও উভয়েই স্বজাতীয়।
একালে জীবনের প্রতি আমাদের দার্শনিক অবজ্ঞা নেই, আছে অন্ধভক্তি। কারণ, জীবন আমাদের পক্ষে এখন আর নিরর্থক নয়। আমরা এখন জানি যে, জীবন হচ্ছে ক্রমবর্ধনশীল, এবং তার চরম সার্থকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। মর্তকে স্বর্গে পরিণত করবার শক্তি মানুষের হাতেই আছে, সুতরাং আমাদের কাম্য পদার্থ মোক্ষ নয়, ভূস্বর্গ। জীবন আজও দুঃখময়, কিন্তু আমাদের পক্ষে পরমপুরুষার্থ হচ্ছে এই দুঃখময় জীবন থেকে পলায়ন করা নয়, তাকে জয় করা। কামনাকে বশ করা জীবনীশক্তির হ্রাস করা, কারণ সে শক্তির যথার্থ কার্য হচ্ছে কাম্য বস্তুকে বশীভূত ও আয়ত্ত করা। এখন আমরা Evolution নামক নূতন বিশ্বকর্মার সন্ধান পেয়েছি, তাই আমরা progress নামক তার চাকা ঘোরানোকে পরমপুরুষার্থ বলে মনে করি। কাল আগে ছিলেন প্রলয়কর্তা, ইভলিউশনের দৌলতে তিনি হয়ে উঠেছেন সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং মানুষের যত প্রকার সাংসারিক প্রয়োজন আছে তার সাধনা করাই এ যুগে যথার্থ মানবধর্ম। ফলে অর্থ কাম আমাদের আরাধ্য বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই এ যুগে আমরা সবাই হয় (conomical, নয় political, নয় social সমস্যার হাতে-কলমে মীমাংসা করবার জন্য ব্যগ্র। ফলে কাব্য আমাদের এইসব প্রচেষ্টার কতদূর সহায় কি অন্তরায়, সেই হিসেব থেকে কাব্যের মূল্য নির্ধারণ করবার প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এসব দিক থেকে কাব্যের সমালোচনা করায় শুধু অল্পবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ এ জাতীয় সমালোচকের মনের কথা হচ্ছে, কাব্য থেকে কি শিক্ষা লাভ করলুম, কি আনন্দ লাভ করলুম, তা নয়। এ জাতীয় সমালোচক সেকালেও ছিল এবং তাদের লক্ষ্য করে দশরূপকার ধনঞ্জয় বলেছেন—
আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্ৰং ফলমল্পবুদ্ধিঃ
যোহপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙ্মুখায়।
এ সংস্কৃত মত আমি শিরোধার্য করি, কেননা এই হচ্ছে অতি-আধুনিক মত। যে মত অতিপুরাতন এবং সেই সঙ্গে অভিনূতন সে মত যদি ভুল হয় তো তা নাছোড় ভুল, অর্থাৎ সত্য।
৮.
রবীন্দ্রনাথ আজকের দিনে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যে আমরা সুশিক্ষা অশিক্ষা কি কুশিক্ষা কোন্ জাতীয় শিক্ষা লাভ করি এ প্রশ্ন অনেক সমালোচক করেছেন এবং সেব প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ তার একখানি কাব্যের উল্লেখ করব, যার উপর অল্পবুদ্ধি সাধু লোকেরা বহু বাণ বর্ষণ করেছেন; যদিচ তাদের মধ্যে অনেকে সেখানি যে যথার্থ কাব্য তা অস্বীকার করতে পারেন নি। সে কাব্যের নাম চিত্রাঙ্গদা। এই চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে প্রতিকুল সমালোচনার সার সংগ্রহ করেছেন টমসন নামক জনৈক ইংরেজ মিশনারি। তার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে–
It is his loveliest dirama; a lyrical feast, though its form is black-verse…. It is almost perfect in unity and conception, magical in expression.
যারা কাব্যের রস উপভোগ করেন তারা এর বেশি কোনো কাব্য সম্বন্ধে আর কি জানতে চান? কিন্তু সাধু ব্যক্তিদের আরও একটি বলবার কথা আছে। এ কাব্য সাধু কি অসাধু তার বিচার তারা না করে থাকতে পারেন না। তাই টমসন বলেছেন
The play was attacked as inmoral, and to this day offends many readers, not all of whom are either fools or milksops.
…. the purpose of the play hias been represented as being the glorification of sexual abandonment.
…. the play, in these earlier passages, repeatedly trembes on the edge of the hog of lubricity.
তার পর এর চাইতেও এ কাব্যের নাকি একটি বড় দোষ আছে। টমসন বলেন–
The most serious charge that can be brought against Chitrangada in against its attitude.
টমসন সাহেবের কৃত চিত্রাঙ্গদা কাব্যের দোষগুণ-বিচারের বিচার করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমি কবির উপর জজিয়তি করতে ভয় পাই, কিন্তু সমালোচকের সঙ্গে ঝগড়া আমি সানন্দে করতে পারি।
৯.
চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানবমনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল বা শক্তি।
অনঙ্গ-আশ্রম হচ্ছে একটি কল্পলোক, যেমন মেঘদূতের অলকা ও কুমারসম্ভবের শৈল-আশ্রম একটি কল্পলোক মাত্র। জিয়োগ্রাফিতে এসব লোকের সন্ধান মেলে না, কারণ মাটির পৃথিবীতে তাদের স্থান নেই, তাদের সৃষ্টি স্থিতি শুধু মানুষের মনে।
মানুষের মন অবশ্য এই পৃথিবী হতে মনোমত উপাদান সংগ্রহ করে এই কল্পলোক রচনা করে; যেমন মানুষে গুটিকতক পার্থিব উপাদান দিয়েই স্বর্গলোক অর্থাৎ সর্বলোককাম্য একটি অপার্থিব কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে।
এই কল্পলোক বাস্তব জগৎ থেকে বিভিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয়। ভালো কথা, আমরা যাকে বস্তুজগৎ বলি সে বস্তুই বা কি? সে জগৎও তো মানুষের মন রচনা করেছে। কবিতার কল্পনোক ও বুদ্ধির প্রকৃত লোক দুইই মানবমনের সৃষ্টি। এ দুয়ের ভিতর যথার্থ প্রভেদ এই যে, এ দুটি মানবমনের দুটি বিভিন্ন শক্তির রচনা। কথাটা শুনে চমকে উঠবেন না। আপাতদৃষ্টিতে যা বাহ্যবস্তু বলে মনে হয় তাকে যাচিয়ে দেখতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় তার। অন্তরে রয়েছে logical mind। আমরা যাকে object বলি তা যে subjectএরই বিকার তা স্বয়ং লজিকই মানতে বাধ্য।
এই বস্তুজগৎ ওরফে মানুষের কর্মভূমির যথার্থ স্রষ্টা হচ্ছে মানুষের কর্মপ্রবৃত্তি। কর্মজগৎ ও কল্পজগৎ এ দুই জগই সমান সত্য, কেননা আমাদের মনে যেমন কর্মের প্রতি আসক্তি আছে তেমনি কর্মজগৎ থেকে মুক্তি পাবারও আকাক্ষা আছে। এই আকাক্ষা চরিতার্থ হয় আমাদের স্বকপোলকল্পিত ধর্মে ও আর্টে। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা যে-জাতীয় স্বপ্ন সে স্বপ্নেরও আমাদের আন্তরিক প্রয়োজন আছে। এ প্রয়োজনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন শুধু সেই জাতীয় বুদ্ধিমান লোকেরা যাদের অন্তর একান্ত বিষয়বাসনার গণ্ডীবদ্ধ, সে বিষয়বাসনা ব্যক্তিগতই হোক আর জাতিগতই হোক। এঁদের মনে কর্মজিজ্ঞাসার অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা নেই। এই একচক্ষু হরিণের দল ভুলে যান যে, মানুষমাত্রই বাস করে কতকটা কর্মজগতে আর কতকটা স্বপ্নলোকে।
১০.
এই স্বপ্নকে যাঁরা সম্পূর্ণ সাকার করে তুলতে পারেন, অর্থাৎ সমগ্র ও পরিচ্ছিন্ন রূপ দিতে পারেন, তারাই হচ্ছেন পূর্ণ আর্টিস্ট। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্য মানুষের যৌবনস্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।
ছবি গান ও কবিতার বিষয় আলোচনা করতে হলেই আমরা ‘সুন্দর’ শব্দটি বারবার ব্যবহার করতে বাধ্য হই— যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা করতে বসলে আমরা বারবার ‘সত্য’ শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হই। অথচ beauty ও truthএর বাচ্য পদার্থের মত অনির্দেশ্য বস্তু আর ভূভারতে নেই। তাই আমরা সৌন্দর্য’ শব্দের বদলে সৌন্দর্যের নানারকম উপকরণের উল্লেখ করি, যথা, মাধুর্য ঔদার্য কান্তি দীপ্তি সুষমা সৌকুমার্য লালিত্য লাবণ্য চমৎকারিত্ব মনোহারিত্ব ইত্যাদি। এ সব নামই সৌন্দর্যের বেনামি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। ফলে এসবের প্রসাদে সৌন্দর্যের অর্থ স্পষ্টতর হয় না, কিন্তু সৌন্দর্য নামক গুণটির অনুভূতি লোকসামান্য। সুতরাং সেই অস্পষ্ট অনুভূতির উপরই আমার এ আলোচনা প্রতিষ্ঠিত করব। আর তা করায় ক্ষতি নেই। কারণ যেসকল দার্শনিক beauty, truth প্রভৃতি শব্দের চুলচেরা বিচার করেন, তারা অনেকেই সোনা ফেলে আঁচলে গিট দেন। অর্থাৎ নামের সন্ধান করতে রূপের সন্ধান হারিয়ে ফেলেন।
কোনো কাব্যের আত্মার পরিচয় দেওয়ার চাইতে তার দেহের পরিচয় দেওয়াটা ঢের সহজ, কেননা দেহ জিনিসটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিচ্ছিন্ন। আর, সকলেই জানেন যে, ভাষা হচ্ছে ভাবের দেহ। নীরব কবি বলে পৃথিবীতে কোনো প্রকার জীব নেই, কেননা এ পৃথিবীতে ভাষাহীন ভাব নেই। সুতরাং আমি যদি চিত্রাঙ্গদার ভাষার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে আশা করি তার আত্মার সাক্ষাৎকার আপনারা আপনা হতেই পাবেন। আমাদের দেশে লোকে ভগবানকে কায়াহীন সত্তা হিসাবে ধারণা করতে পারতেন না, তাই বৌদ্ধরা তাকে ধর্ম-কায় ও বৈষ্ণবেরা মন-কায় বলে উপলব্ধি করতেন। সুতরাং কাব্যকে ভাষা-কায় বলায় আমরা কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে নাস্তিক অথবা দেহাত্মবাদী বলে অন্ততঃ এ দেশে গণ্য হব না।
১১
কবিকঙ্কণ বলেছেন যে, চণ্ডীকাব্য তিনি লেখেন নি কিন্তু চণ্ডী তাঁর হাত ধরে লিখিয়েছেন। ভারতচন্দ্রও ঐ একই কথা বলেছেন। তিনিও অন্নপূর্ণার আদেশে ও প্রসাদে অন্নদামঙ্গল রচনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ চণ্ডী এ অন্নপূর্ণা সরস্বতী ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা নন। কবিকঙ্কণ সরস্বতীর গুণ-বর্ণনা করতে একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন যে তাঁর–
বীণাগুণে তরল অঙ্গুলি।
কবিকঙ্কণের অঙ্গুলি কিন্তু তরল নয়, স্কুল। আর ভারতচন্দ্রের অঙ্গুলি লঘু হলেও সে অঙ্গুলি কখনো বীণাগুণ স্পর্শ করে নি, কারণ তার অঙ্গুলি ছিল মেজরাপ-মণ্ডিত। চিত্রাঙ্গদার কবির অঙ্গুলি যে বীণাগুণে পূর্ণমাত্রায় তরল তা যার ভাষার সুরের কান আছে তিনি চিত্রাঙ্গদার দু লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন। চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। এর কোথাও একটি বেসুরো কথা নেই, আর এ ভাষার গতি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সলীল। ও-কাব্যের অন্তরে যেমন একটিও বেসুরো কথা নেই তেমনি একটিও উচ্ছল ছত্র নেই। এ কাব্যের ধ্বনি এক মুহূর্তের জন্যও বাণীকে ছাপিয়ে কিংবা ছাড়িয়ে ওঠে নি। ভাষার সমতা ও ধ্বনির মসৃণতা গুণে চিত্রাঙ্গদা মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের স্বজাতীয় ও সমকক্ষ। এ ভাষা যেমন প্রসন্ন তেমনি সপ্রাণ, যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। এ ভাষা পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে মুক্ত ছন্দে অবলীলাক্রমে বয়ে যাচ্ছে। এ প্রবাহিণীর সুর ললিত, তাল মধ্যমান। এ কাব্য সরস্বতী নিজ হাতে লিখেছেন বললে আমরা সে কথায় অবিশ্বাস করতুম না।
ভারতচন্দ্র স্থানান্তরে বলেছেন যে, অন্নদা তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে–
যে কবে সে হবে গীত, আনন্দে লিখিবে।
চিত্রাঙ্গদার কবি, যার মুখ দিয়ে যা বলেছেন তা সবই গীত হয়েছে। এ ভাষা কবির মুখে স্বয়ং বসন্ত দিয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদা বসন্তের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে–
বড় ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছ্বাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্বপুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন!
হে বসন্ত, হে বসন্তসখে, সে বাসনা
পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে।
বসন্তসমীরণের স্পর্শে চিত্রাঙ্গদার দেহের অনুরূপ চিত্রাঙ্গদা কাব্যেরও দেহ অপূর্ব পুলকভরে ফুটে উঠেছে। এ ভাষা নবীন প্রাণের স্পর্শে আগাগোড়া মুকুলিত ও পুলকিত।
১২
আমাদের নিত্যকর্মের ভাষার সঙ্গে কবির ভাষার যে একটি স্পষ্ট প্রভেদ আছে, তা সকলেই জানেন। দৈনিক সংবাদপত্রের ইংরেজি ভাষা ও শেক্সপীয়ারের ভাষা যে এক নয়, তা যে-কোনো সংবাদপত্রের এক পৃষ্ঠা পড়বার পর শেক্সপীয়ারের নাটকের এক পৃষ্ঠা পড়লেই সকলের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। প্রভেদ যে ঠিক কোথায় তা বলা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে উপায়ান্তরের অভাবে আমরা নানারূপ বিশেষণের আশ্রয় নিই। কিন্তু সেসব বিশেষণের সার্থকতাও অনুভূতিসাপেক্ষ। যে-কোনো বিষয়ের আমরা ব্যাখ্যা শুরু করি নে কেন, লজিকের সাহায্যে কতক দূর অগ্রসর হবার পর আমরা দেখতে পাই যে, লজিকের হাত ধরে আর বেশি। দূর এগনো চলে না। কেননা তখন আমরা এমন-একটি সত্যের সাক্ষাৎলাভ করি যার নাম mystery। এর কারণ ভগবান কৃষ্ণ বলে দিয়েছেন–
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
এই ব্যক্তমধ্যই লজিকের এলাকা। আমরা যদি বলি কবির ভাষায় প্রাণ আছে, তাহলে বলা হয় যে, কবির ভাষা অনির্বচনীয়; কেননা প্রাণ পদার্থটিও একটি mystery, তবে উপমার সাহায্যে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করা যায়। আমাদের কর্মের ভাষা static, অর্থাৎ পদার্থের নামকরণ করেই তার কর্মের অবসান হয়; কবির ভাষা dynamic, অর্থাৎ সে ভাষার অন্তরে গমক আছে, অকবির ভাষার অন্তরে তা নেই। আলংকারিকরা বলেছেন
ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্
যদি শব্দহবয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।
কবির মুখনিঃসৃত এই শব্দাখ্য-জ্যোতি মনের নানাদেশে সঞ্চারিত হয় এবং নানা ভাবকে অঙ্কুরিত করে; ফলে আমাদের মনোজগতের প্রাণের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দেয়। কবির বাণী তাব অন্তপূঢ় শক্তির বলে কি বাহ্যজগৎ কি অন্তর্জগতের বিরাট অব্যক্ত অংশের রহস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। চিত্রাঙ্গদার ভাষা সেই জাতীয় জাদুকরী ভাষা, যার সাক্ষাৎ আমরা ইংরেজ কবি কীটসের কবিতায় পাই। এক কথায় এ হচ্ছে লৌকিক ভাষার অলৌকিক সংস্করণ। এ ভাষার মোহিনীশক্তির মূল হচ্ছে কবির আত্মায়। সে যাই হোক, ভাষার সঙ্গে কাব্যের এতটা আত্মীয়তা আছে যে, ইউরোপে অনেকে কবিকে a great voice বলে আখ্যা দিয়েছেন—
১৩.
প্রাচীন আলংকারিকদের মতে কাব্যের সৌন্দর্য নগ্ন নয়, অলংকৃত। এমন কি তাদের মতে–
কাব্য গ্রাহ্যমলংকারাৎ।
যে অলংকারের গুণে কাব্য গ্রাহ্য সে গুণটি কি? বামনাচার্য বলেছেন যে–
সৌন্দর্যমলংকারঃ।
সৌন্দর্য অর্থ অলংকার, আর অলংকার অর্থ সৌন্দর্য; এ রকম ব্যাখ্যা শুনে এ বিষয়ে আমরা যে তিমিরে আছি সেই তিমিরে থেকে যাই। আমি বালককালে একটি বঙ্গদেশীয় মুসলমানের মুখে একটি ‘হররা ঘোড়ার কথা শুনি। হররা’ অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করলেন ‘বোরা। তার পর ‘বোর’ কাকে বলে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন ‘মুসকি। এইরূপ ব্যাখ্যা শুনে আমি অবশ্য তার আরবি ও ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট তারিফ করি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার ধারণা হয় ভদ্রলোক কি বলতে চান তা তিনি নিজেও জানেন না, কেননা যদি জানতেন তো ও-রঙের বাংলা নামটাই বলে দিতেন। সুতরাং বামনাচার্য যখন অলংকার শব্দ কি connote করে তা বলতে না পেরে কি denote করে তাই বললেন, তখন তার বক্তব্য বোঝা গেল। যখন শুনলুম–
পুনরলংকার শব্দোহয়মুপমাদিষু বৰ্ততে
তখন নিশ্চিন্ত হলুম।
আমার বন্ধু শ্ৰীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যজিজ্ঞাসা নামক একটি অতি সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাংলায় লিখেছেন। সে প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, নব্য আলংকারিকদের মতে উপমাদি অলংকারের প্রাচুর্য সত্ত্বেও বাক্য কাব্য হয় না, অপর পক্ষে বহু অনলংকৃত বাক্য চমৎকার কাব্য। এর প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে দেদার আছে। কিন্তু অলংকার যে কাব্যকে শোভাহীন করে এমন কথা কোনো আলংকারিক বলতে পারেন না, তা তিনি যতই নব্য হোন-না। কেন। কেননা, উপমাদি যদি কাব্যদেহের কলঙ্ক হত তাহলে কালিদাসের কাব্য পা থেকে মাথা পর্যন্ত কলঙ্কিত। অতএব কোন স্থলে কিরূপ উপমাদি প্রকৃতি-সুন্দর কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক।
আমি এ স্থলে শুধু দুটি মূল অলংকারের কথা বলব। একটি অনুপ্রাস, অপরটি উপমা। সংস্কৃত মতে একটির নাম শব্দালংকার, অপরটির নাম অর্থালংকার। কিন্তু এ উভয়ই মূলতঃ সমধর্মী। দণ্ডী বলেছেন–
যয়া কয়াচিচ্ছ ত্যা যৎ সমানমনুভূয়তে।
তদ্রূপাহি পদাসত্তিঃ সানুপ্রাসা রসাবহ।
তার পর
যথাকথাঞ্চিৎ সাদৃশ্যং যত্ৰোদ্ভূতং প্রতীযতে
উপমা নাম সা তস্যাঃ প্রপঞ্চোহয়ং নিদর্শতে।
অর্থাৎ এক অলংকারের প্রসাদে কানের কাছে শব্দসমূহ সমান অনুভূত হয়, অপর অলংকারের প্রসাদে মনের কাছে বস্তুসদৃশ প্রতীয়মান হয়।
এ বিশ্বে আমাদের আপাতদৃষ্টিতে যা বিভিন্ন তার সমীকরণ করাই হচ্ছে কাব্যের ধর্ম, অর্থাৎ যা-কিছু পরস্পরবিচ্ছিন্ন তাদের নিরবচ্ছিন্ন রূপ দিতে আর প্রক্ষিপ্ত জগৎকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে শুধু কবি প্রতিভা। পরাবিদ্যা যেমন আমাদের লৌকিক ভেদবুদ্ধি নষ্ট করে, কাব্যও তেমনি আমাদের লৌকিক ভেদদৃষ্টি নষ্ট করে। এই বিশ্বে বহুর সম প্রাণতা ও আত্মীয়তার অনুভূতিই হচ্ছে মুক্তির রসাস্বাদ। কারণ যে মুহূর্তে ভেদবুদ্ধি অপসারিত হয় সেই মুহূর্তে অহং আত্মা হয়ে ওঠে।
আমার এ ধারণা যদি সত্য হয় তো বলা বাহুল্য যে, অনুপ্রাস ও উপমা দুইই কাব্যের বিশেষ অন্তরঙ্গ। কারণ দৃশ্যজগৎ ও শব্দজগতের নিগূঢ় সত্য ব্যক্ত করাই এদের ধর্ম। এই দুই যখন কাব্যে অন্তরঙ্গ না হয়ে বাহ্য অলংকার হয় তখনই তা অগ্রাহ্য। ভাষার ও ভাবের খেলে জমির উপর উপমা-অনুপ্রাসের চুমকি বসানো শুধু মন্দ কবির কারদানি। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের অনু পাস ও উপমা উভয়ই ও-কাব্যের অন্তরঙ্গ। এ কাব্যে এমন একটি ও অনুপ্রাস কিংবা উপমা নেই যা এ কাব্য-অঙ্গে প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্তর থেকে উদ্ভূত নয়। সংগীতে যেমন সেই তানের চমৎকারিত্ব আছে যে তান রাগিণীর প্রাণ থেকে স্বতঃ-উৎসারিত, তেমনি চিত্রাঙ্গদা-রূপ রাগিণীর অন্তরে বহু অনুপ্রাস আছে যা উক্ত রাগিণীর অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে–
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শম্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে…
শেফালিবিকীর্ণতৃণ বনস্থলী দিয়ে…
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্থ ক্ষীণতমুলতা
পরাবলম্বিত লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা…
এসব অনুপ্রাস যে চমৎকার তার সাক্ষী কান। কিন্তু এসব অনুপ্রাস অযত্নসুলভ। ধ্বনি আপনিই দানা বেঁধে উঠেছে সমগ্ৰ সংগীতপ্রাণ কাব্যের অন্তর হতে। টন সাহেব বলেছেন যে, এ কাব্য magical in expression, যদিচ তা অমিত্রাক্ষরে রচিত। এ কাব্যে যে অন্ত-অনুপ্রাস নেই তার কারণ। সমগ্র কাব্যখানিই একটি একটানা অনুপ্রাস।
১৪
আসল কথা এই যে, অলংকার হচ্ছে কাব্যের একরূপ ভাষা। নব্য আলংকারিকরা অলংকারের জাতিভেদ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে অতিশয়োক্তি হচ্ছে একমাত্র অলংকার। প্রাচীনেরাও এ অলংকারকে সর্বোত্তম অলংকার বলে গণ্য করেছেন। এ অলংকার যে কি, তা প্রাচীন আলংকারিকদের মুখেই শোনা যাক–
বিবক্ষা যা বিশেষস্য লোকসীমাতিবর্তিনী
অসাবতিশয়োক্তিঃ স্যাদলংকারোত্তমা যথা।
লোকসীমাত্তিবৃত্তস্য বস্তুধর্মস্য কীর্তনম্
ভবেতিশয়ো নাম সম্ভবোহসম্ভবে দ্বিধা।
চিত্রাঙ্গদা কাব্যের উপমা-রূপকাদি উক্ত অর্থে অতিশয়োক্তি, অর্থাং তাদের গুণে বর্ণিত বিষয় সব লোকসীমা অতিক্রম করে, ইংরেজিতে যাকে বলে, transcend করে। এই সর্বোত্তম অলংকারের স্পর্শে সমগ্র কাব্যশরীরের রূপলাবণ্যও লোকোত্তর হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ যা natural তা supernatural বলে প্রতিভাত হয়। আমি নিম্নে চিত্রাঙ্গদা থেকে দু-চারটি ঐ জাতীয় উক্তি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তাদের নাম উপমাই হোক, রূপকই হোক, আর উৎপ্রেক্ষাই হোক, তার প্রতিটি যে অপূর্ব অতিশয়োক্তি সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। চিত্রাঙ্গদা মদনের বরে ক্ষণিকের জন্য ফুলের মত ফুটে উঠে বলেছেন
যেন আমি ধরাতলে
এক দিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা
পরমায়ু-তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের
আনন্দমর্মর, পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদি-অন্ত-হারা।
এমন সুন্দর এমন মর্মস্পর্শী পরিপূর্ণ যৌবনের কুসুমকাহিনী আর কোনো কবির মুখে কেউ কখনো শুনেছেন?
১৫.
পুষ্পরাজ্যেও আবিষ্কৃত আর-একটি উপমার পরিচয় দিই। চিত্রাঙ্গদা যেদিন তার সদ্যঃ প্রস্ফুটিত অলোকসামান্য রূপের প্রথম সাক্ষাৎ পান—
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরকবয়স
যাপিল নয়ন মুদি; যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শশাভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।
এই শব্দচিত্রের দিকে সহৃদয় ব্যক্তি চিরকাল ‘রহিবে চাহিয়া সবিস্ময়ে’।
আলংকারিকদের মতে কবির যে জাদুমন্ত্রের বলে সাদৃশ্য সাযুজ্যে similarity identityতে পরিণত হয় সেই উক্তিই অতিশয়োক্তি। তাঁরা উদাহরণস্বরূপ বক্ষ্যমাণ শ্লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন–
মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্বাঙ্গীণাচনাঃ
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ।
অর্থাৎ অভিসারিকা জ্যোৎস্নার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন, কেননা তিনি মল্লিকার মালা ধারণ করেছেন, সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করেছেন, এবং ক্ষৌমবাস পরিধান করেছেন। এখন চিত্রাঙ্গদার বিষয়ে কবির একটি উক্তি শোনা যাক—
উষার কনকমেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায় পূর্বপর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে।
এ কবির সাক্ষাৎ পেলে প্রাচীন আলংকারিকদের যে দশা ধরত সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এরূপ উক্তির চিত্রাঙ্গদায় আর অন্ত নেই। এ ক্ষেত্রে আমি আলংকারিকদের ভাষায় বলতে বাধ্য হচ্ছি ‘স্বয়ং পশ্য বিচারয়’। এখানে আর দুটি মাত্র উপমার উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি নে। চিত্রাঙ্গদা সুপ্ত অজুনের সম্বন্ধে বলেছেন–
শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলা-সম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ…
দ্বিতীয়টি অর্জুনের উক্তি
তুমি ভাঙিয়াছ ব্ৰত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।
উক্ত কথা ক’টিতে কবির বাণী তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। সনকুমার নারদকে বলেছিলেন, ‘অতিবাদী হও; আর লোকে যদি তোমাকে অতিবাদী বলে তো বোলো যে, হাঁ আমি অতিবাদী। কবিমাত্রই অতিবাদী। আর এই ‘অতি’ শব্দের মর্ম যিনি গ্রহণ করতে পারেন তিনিই মর্মে মর্মে অনুভব করবেন যে, চিত্রাঙ্গদার কবি চরম কবি।
১৬
আমি পূর্বে বলেছি, চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। টসন সাহেব এ কথা অস্বীকার করেন নি, কেননা তিনি বলেছেন It is a lyrical feast। কিন্তু উক্ত feast উপভোগ করে নাকি মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কারণ উক্ত রাগিণীর অস্থায়ী erotic এবং অন্তরা immoral।
যদি ধরে নেওয়া যায় যে, কবিতা সংগীতের স্বজাতীয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি, কানাড়া moral এবং কেদারা immoral, ভূপালী শ্লীল ও ভৈরবী অশ্লীল এ রকম কথা বলায় ছন্নতা ও মূখতা ছাড়া আর কিসের পরিচয় দেওয়া হয়?
যদি এ মত কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত টসনের মত হত তাহলে এ বিষয়ে। কোনো কথা বলবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আর্টের moralityর বিচার করতে অনেকে সদাই উৎসুক। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের পক্ষে মর্যালিটি অত্যাবশ্যক এবং সেই কারণে জীবনের এই অত্যাবশ্যক বস্তুটি আমরা সর্বত্রই খুজতে চাই। চুরি করা যে অধর্ম, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। যার নিজে চুরি করতে আপত্তি নেই, তিনিও তার জিনিস পরে চুরি করলে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেন।
–মৃচ্ছকটিক নাটকে পরের ঘরে সিদ কেটে চুরির একটি চমৎকার বর্ণনা আছে এবং শৰ্বিলকের মুখে চুরিবিদ্যার একটি সরস গুণকীর্তন আছে। যা মানুষ মাত্রেরই মতে iinnoral, সেই বিষয় নিয়ে কবি তাঁর কল্পনা খাঁটিয়েছেন, অথচ অদ্যাবধি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সংস্কৃত সাহিত্য হতে মৃচ্ছকটিকের ও-অংশ বহিষ্কৃত করবার প্রস্তাব করেন নি। এর কারণ কি? এর কারণ সমাজে যা অধর্ম, কাব্যে। তা রসে পরিণত হয়েছে। ফলে মৃচ্ছকটিক পড়ে কারও মনে চুরি করবার প্রবৃত্তি জন্মায় নি। মর্যালিটি হচ্ছে মানুষের ব্যাবহারিক আত্মার জিনিস, আর কাব্য তার অন্তরাত্মার। এই অন্তরাত্মার সঙ্গে ব্যাবহারিক আত্মার প্রভেদ কি তা জানতে চান তো দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করুন। কাব্যের যে জীবনের উপর কোনো প্রভাব নেই, এ কথা অবশ্য আমি বলতে চাই নে; কাব্যের আবেদন মানুষের moral senseএর কাছে নয়, spiritual senseএর কাছে। যা স্পিরিচুয়াল হিসাবে অমৃত তা যে মর্যাল হিসাবে বিষ এ কথা শশাভা পায় শুধু জড়বুদ্ধির মুখে। বরং মানুষে চিরকাল এই বিশ্বাস করে এসেছে যে, মনের স্পিরিচুয়াল থোক মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধন করে। এ বিশ্বাস ভ্রান্তি নয়।
১৭
চুলোয় যাক অন্তরাত্মা। ব্যাবহারিক আত্মার দিক থেকেই দেখা যাক। কবির স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ধারণা (attitude) কি হিসেবে জঘন্য? তা যে ঘৃণ্য সে কথা রোলো Bollo নামক অপর একটি অধ্যাপক স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। তার কথা হচ্ছে এই : one hates the view; এবং টসন এ কথা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কবির মতে নাকি woman exists for man’s sake; চিত্রাঙ্গদার শেষ কথাগুলিই নাকি কবির মনের কথা। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে তাই।
চিত্রাঙ্গদার শেষ নিবেদন এই যে, তিনি অর্জুনের শুধু প্রণয়িনী নয় তার সহধর্মিণীও হতে চেয়েছিলেন। এই সহধর্মিণীর আদর্শ নাকি সেকালের অসভ্যদের আদর্শ, হিন্দুদের আদর্শ। কিন্তু একালের সভ্য মানবের, অর্থাৎ ইংরেজের, আদর্শ হচ্ছে স্ত্রীলোকের পুরুষের সহধর্মী হওয়া। পিতা যখন চিত্রাঙ্গদাকে পুত্র করেছিলেন তখন অজুনের কর্তব্য ছিল তাঁকে ভ্রাতা করা। তাহলেই টমসন এবং রোলোর কাছে এ কাব্য জঘন্য না হয়ে বরেণ্য হত।
যখন এঁদের মুখে এসব বুলি শুনি, তখনই মনে হয় যে, বর্তমান সভ্যতার বুলিগুলি যেমন সাধু তেমনি ভুয়ো। Equality of the sexes বহুলোকের মুখে একটি সম্পূর্ণ নিরর্থক কথা, কেননা এ ক্ষেত্রে সাম্যের সঙ্গে ঐক্য শব্দের অর্থের প্রভেদের প্রতি তারা নজর দেন নি। Woman exists for man’s sake এ কথাটা তেমনি হাস্যকর যেমন man exists for woman’s sake কথাটা হাস্যকর। সত্য কথা এই যে, এই দুটো কথাই আংশিক হিসাবে সত্য। টমসন পরে বলেছেন যে, individual rights of womenএ চিত্রাঙ্গদার কবি বিশ্বাস করেন না। যদি তিনি না করেন, তার। কারণ, অপরের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ইডিভিজুয়াল বলেও কোনো জীব নেই; অতএব তার কোনো রাইট্ও নেই। অধিকার কর্তব্য ইত্যাদি সামাজিক মানবের কথা, সুতরাং প্রতি অধিকারের সঙ্গেসঙ্গেই অসংখ্য কর্তব্যবন্ধন আছে। স্ত্রীজাতিকে তার মনের ও জীবনের নানারূপ বন্ধন থেকে মুক্ত করে আমরা womanকে man করতে পারব না, পারব শুধু তাকে female করতে, কারণ instinctএর বন্ধন থেকে কোনো জীবকে মুক্ত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। টমসন যে-সভ্যতার মুখপাত্র সে-সভ্যতার বোধ হয় এই বিশ্বাস যে, স্ত্রীলোককে কোনো রকমে দ্বিতীয় পুরুষ করতে পারলেই বিশ্বমানব উত্তম পুরুষ হয়ে উঠবে।
স্ত্রীজাতি যে মানুষ হিসাবে পুরুষ জাতির equal খৃস্টধর্মাবলম্বীরা এ সত্যের সন্ধান যুগযুগান্তরের পরে পেয়েছে। বাইবেলের মতে নারী আদিম মানবের একখানি পাঁজরার হাড় হতে সৃষ্ট। যুগ যুগ ধরে তারা এ কথা বেদবাক্য জ্ঞানে মেনে এসেছে। অতঃপর তাদের যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল তখন তারা সেই অস্থিজ জীবকে আবার মানুষ করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল এবং তাদের কাছে যথার্থ মানুষ হচ্ছে পুরুষমানুষ। তাই তারা কাজে না হোক কথায় বিধির নিয়ম উলটে দিতে চায়। হিন্দুর কল্পনা কিন্তু চিরকালই বিভিন্ন। কালিদাস বলেছেন–
স্ত্রীপুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্তেঃ সিসৃক্ষয়।
প্রসূতিভাজঃসর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ।।
এ শুধু কবিকল্পনা নয়, ধর্মশাস্ত্রের ঐ একই কথা। মনু বলেছেন–
দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমনে পুরুষোভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমজৎপ্রভুঃ।
১৮
মদন চিত্রাঙ্গদাকে বলেছিলেন—
আমিই চেতন ক’রে দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।
এই কাব্য এই শুভ পুণ্যক্ষণের কল্পনা। এবং কবিপ্রতিভার বলে এ পুণ্যমুহূর্ত একটি অনন্ত মুহূর্ত হয়ে উঠেছে। যা জীবনে ক্ষণিকের, তাকেই মনোজগতে চিরদিনের করবার কৌশলের নামই আর্ট।
বসন্ত বলেছেন–
একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন…
আর মদন–
সংগীতে যেমন, ক্ষণিকের
তানে, গুঞ্জরি কঁদিয়া ওঠে অন্তহীন
কথা।
চিত্রাঙ্গদা কাব্যের মর্মকথা মদন ও বসন্তই অমরবাণীতে বলে দিয়েছেন।
যে দেব ‘নারীরে হইতে নারী পুরুষে পুরুষ’ চেতন করে দেয় তার গ্রীক নাম Eros, এবং এই কারণেই পূর্বোক্ত শ্রেণীর সমালোচকরা এ কাব্যকে erotic বলেন।
এখন ইংরেজি ভাষায় এ শব্দটি হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। Erotic loveএর বাংলা আমি জানি নে, সম্ভবতঃ তারা যাকে platonic love বলেন, এ love তার উলটো। এবং এই জাতীয় সমালোচকদের কাছে উক্ত কারণে চিত্রাঙ্গদা অশ্লীল। এখন, এ কাব্য শ্লীল বা অশ্লীল সে বিচার করবার একটি বাধা আছে। চিত্রাঙ্গদা যে অশ্লীল নয় তা প্রমাণ করতে হলে আমার যুক্তি সব অশ্লীল হয়ে পড়বে, আর আমি যখন দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা করছি নে, তখন শ্লীলতার সামাজিক বন্ধন লঙ্ঘন করবার আমার কোনো অধিকার নেই। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সৌন্দর্য, সত্য নয়; সুতরাং এ ক্ষেত্রে রুচির কথাটা বড় কথা। ‘
Love বিষয়ে শ্লীলতা রক্ষা করে আলোচনা করা যে অসম্ভব তার সাক্ষী স্বয়ং প্লেটো। তাঁর যে পুস্তক থেকে প্লেটনিক লভ্-এর কিংবদন্তী জন্মগ্রহণ করেছে সেই Bauquet নামক অপূর্ব দার্শনিক বিচার বাংলায় কথায় কথায় অনুবাদ করা চলে না, কারণ অদার্শনিক পাঠকদের কাছে তা ঘোর অশ্লীল বলে গণ্য হবে। প্লেটনিক লভ্-এর বিচারই যদি এতাদৃশ ভয়াবহ হয়, ত অ-প্লেটনিক লভ্-এর বিচার যে বীভৎস হবে তা বলাই বাহুল্য।
১৯
প্লেটনিক লভ্ একটি আকাশকুসুম। সুতরাং এক দলের লোকের কাছে তা যেমন বিক্রপের বিষয়, অপর আর-এক দল লোকের কাছে তা তেমনি শ্রদ্ধার বিষয়। এখন, উক্ত মতের ভক্তদের জিজ্ঞাসা করি, কুসুম মাত্রই কি আকাশকুসুম নয়। গাছের মূল থাকে মাটিতে, কিন্তু তার ফুল ফোটে আকাশে। ফুল দেখবামাত্র যে-লোকের তার মূলের কথাই বেশি করে মনে পড়ে সে ফুলের যথার্থ সাক্ষাৎ পায় না, পায় শুধু মাটির। সুন্দরের হিসেব থেকে ফুল আকাশকুসুম মাত্র, এবং তাতেই তার সার্থকতা; কিন্তু সত্যের হিসেব থেকে তা সমগ্র সৃষ্টিকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুসূত। আমরা যাকে প্রেম বলি, তাও মনোজগতের বস্তু হলেও দেহের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। যেমন পার্থিব ফুলের রূপ তার একমাত্র গুণ নয়, উপরন্তু তার প্রাণ আছে; তেমনি মানবপ্রেম শুধু চিদাকাশের কুসুম নয়, দেহ ও মন উভয় জগৎ অধিকার করেই তা বিরাজ করে। তার পর দেহ-মনের বিভাগটা কি তেমন সুনির্দিষ্ট? দেহের কোথায় শেষ ও মনের কোথায় আরম্ভ, তা কি আমাদের প্রত্যক্ষ?
ভারতচন্দ্র বলেছেন–
ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ নর-নারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে দোঁহে নানা খেলা করে।
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম সব জীবের অন্তরে
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে দেহিদেহ রূপ ধরে।
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া একি করে চরাচরে।।
যদি কোনো কবির কল্পনায় দেহ-দেহীর ভেদাভেদজ্ঞান মূর্ত হয়ে ওঠে তাহলে সে কবির কল্পনাকে কি শুধু দৈহিক বলা চলে? যা কেবলমাত্র দৈহিক তার অন্তরে সত্য আছে কিন্তু সৌন্দর্য নেই। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর-একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তার বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু, কামলোকের নয়, তা যার অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাদের তা নেই, অর্থাৎ যারা অন্ধ, তাদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।
অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–
কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে। এক-
বিন্দু স্বর্গ শুধু, ভূমিতলে ভুলে প’ড়ে
গেছে?
চিত্রাঙ্গদা
তাই বটে।
এ কাব্য সম্বন্ধে এই শেষ কথা। Erotic কাব্য বলে কোনো বস্তু নৈই, কেননা যে মুহূর্তে কবির কল্পনা কাব্য-আকার ধারণ করে সেই মুহূর্তেই তা eroticism অতিক্রম করে। আমি পূর্বে বলেছি চিত্রাঙ্গদা, মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের স্বজাতি এবং মেঘদূত ও কুমারের মতই তা কাব্যজগতে অমর। চিত্রাঙ্গদা একাধারে কাব্য, চিত্র ও সংগীত, অতএব তা চরম কাব্য। কেননা চিত্রাঙ্গদায় আর্টের ত্রিধারার পূর্ণ মিলন হয়েছে। আর্ট হিসাবে চিত্রাঙ্গদার আর-একটি মহাগুণ তার পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন আয়তন, এর অস্থায়ী-অন্তরার পর যদি আভোগ-সঞ্চারী থাকত, অর্থাৎ এ স্বপ্ন যদি আরও বিস্তৃত হত, তাহলে পাঠকের মন স্বপ্নলোক হতে সুষুপ্তিলোকে চলে যেত।
১৩৩৪ চৈত্র
চুটকি
সমালোচকেরা আমার রচনার এই একটি দোষ ধরেন যে, আমি কথায়কথায় বলি হচ্ছে। এটি যে একটি মহাদোষ সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই; কেননা, ওকথা বলায় সত্যের অপলাপ করা হয়। সত্যকথা বলতে গেলে বলতে হয়, বাংলায় কিছু হচ্ছে না। এদেশের কর্মজগতে যে কিছু হচ্ছে না, সে তো প্রত্যক্ষ; কিন্তু মনোজগতেও যে কিছু হচ্ছে না, তার প্রমাণ বর্ধমানের গত সাহিত্যসম্মিলন।
উক্ত মহাসভার পঞ্চ সভাপতি সমস্বরে বলেছেন যে, বাংলায় কিছু হচ্ছে না দর্শন, না বিজ্ঞান, না সাহিত্য, না ইতিহাস।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রধান বক্তব্য এই যে, আমরা না-পাই সত্যের সাক্ষাৎ, না-করি সত্যাসত্যের বিচার। আমরা সত্যের স্রষ্টাও নই, দ্রষ্টাও নই; কাজেই আমাদের দর্শন-চর্চা realও নয়, criticalও নয়।
অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, কি মত-বিজ্ঞান কি ‘অমত-বিজ্ঞান’, এ দুয়ের কোনোটিই বাঙালি অদ্যাবধি আত্মসাৎ করতে পারে নি; অর্থাৎ বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগও আমাদের হাতে পড়ে নি, তার তন্ত্রভাগও আমাদের মনে ধরে নি। আমরা শুধু বিজ্ঞানের স্থূলসূত্রগুলি কণ্ঠ করেছি, এবং তার পরিভাষার নামতা মুখস্থ করেছি। যে বিদ্যা প্রয়োগপ্রধান, কেবলমাত্র তার মন্ত্রের শ্রবণে এবং উচ্চারণে বাঙালিজাতির মোক্ষলাভ হবে না। এককথায় আমাদের বিজ্ঞানচর্চা real নয়।
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে ইতিহাস-চর্চার উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার এবং উদ্ধার; এ সত্য নিত্য এবং গপ্ত সত্য নয়, অনিত্য এবং লুপ্ত সত্য। অতএব এ সত্যের দর্শন লাভের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক। অতীতের জ্ঞানলাভ করবার জন্য হীরেন্দ্রবাবুর বর্ণিত বোধির (intuition) প্রয়োজন নেই প্রয়োজন আছে শুধু শিক্ষিত বুদ্ধির। অতীতের অন্ধকারের উপর বৃদ্ধির আলো ফেলাই হচ্ছে ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্তব্য, সে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয়। অথচ আমরা সে অন্ধকারে শুধু ঢিল নয়, পাথর ছড়ছি। ফলে পর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের ঐতিহাসিকদের দেহ পরস্পরের শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছে। এককথায় আমাদের ইতিহাসচর্চা critical নয়।
অতএব দেখা গেল যে, সম্মিলনের সকল শাখাপতি এবিষয়ে একমত যে, কিছু হচ্ছে না। কিন্তু কি যে হচ্ছে, সেকথা বলেছেন স্বয়ং সভাপতি। তিনি বলেন, বাংলাসাহিত্যে যা হচ্ছে, তার নাম চুটকি। একথা লাখ কথার এক কথা। সকলেই জানেন যে, যখন আমরা ঠিক কথাটি ধরতে না পারি, তখনই আমরা লাখ কথা বলি। এই ‘চুটকি’-নামক বিশেষণটি খুঁজে না পাওয়ায় আমরা বগসরস্বতীর গায়ে ‘বিজাতীয় ‘অভিজাতীয়’ ‘অবাস্তব’ ‘অবান্তর’ প্রভৃতি নানা নামের ছাপ মেরেছি, অথচ তার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারি নি।
তার কারণ, এসকল ছোট-ছোট বিশেষণের অর্থ কি, তার ব্যাখ্যা করতে বড়-বড় প্রবন্ধ লিখতে হয়; কিন্তু চুটকি যে কি পদার্থ, তা যে আমরা সকলেই জানি, তার প্রমাণ হাতে-হাতেই দেওয়া যায়।
শ্ৰীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিভাষণ যে চুটকি নয়, একথা স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয়ও স্বীকার করতে বাধ্য; কেননা, একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভাবে ও ভাষায় এর চাইতে ভারি অঙ্গের গদ্যবন্ধ জমানির বাইরে পাওয়া দুষ্কর।
হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণও চুটকি নয়। তবে শাস্ত্রীমহাশয় এ মতে সায় দেবেন কি না জানিনে; কেননা, হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ একে সংক্ষিপ্ত তার উপর আবার সহজবোধ্য, অর্থাৎ সকল দেশের সকল যুগের সকল দার্শনিক তত্ত্ব যেপরিমাণে বোঝা যায়, হীরেন্দ্রবাবুর দার্শনিক তত্ত্বও ঠিক সেই-পরিমাণে বোঝ যায় তার কমও নয় বেশিও নয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে যে-কাব্য মহাকায় তাই হচ্ছে মহাকাব্য। গজমাপে যদি সাহিত্যের মর্যাদা নির্ণয় করতে হয়, তাহলে হীরেন্দ্রবাবুর রচনা অবশ্য চুটকি; কেননা, তার ওজন যতই হোক না কেন, তার আকার ছোট।
অপরপক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের অভিভাষণযুগল যে চুটকি-অঙ্গের, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
শাস্ত্রীমহাশয়ের নিজের কথা এই—’একখানি বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব ততদিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে, এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব’— এরকম যাতে হয় না, তারই নাম চুটকি। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি, বাংলায় এরকম ক’জন পাঠক আছেন যাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রবন্ধ পড়ে তাঁদের ভিতরটা সব ওলটপালট হয়ে গেছে।
শাস্ত্রীমহাশয় বাংলাসাহিত্যে চুটকির চেয়ে কিছু বড় জিনিস চান। বড় বইয়ের যদি ধর্মই এই হয় যে, তা পড়বামাত্র আমাদের মনের ভাবের আমল পরিবর্তন হয়ে যাবে, তাহলে সেরকম বই যত কম লেখা হয় ততই ভালো; কারণ দিনে একবার করে যদি পাঠকের অন্তরাত্মার আমূল পরিবর্তন ঘটে, তাহলে বড় বই লেখবার লোক যেমন বাড়বে, পড়বার লোকও তেমনি কমে আসবে। তিনি চুটকির সম্বন্ধে যে দুটি ভালো কথা বলেন নি তা নয়, কিন্তু সে অতি মুরবিয়ানা করে। ইংরেজেরা বলেন, স্বল্পস্তুতির অর্থ অতিনিন্দা। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ চুটকি সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের পক্ষে একটু যাচিয়ে দেখা দরকার। তিনি বলেন, চুটকির একটি দোষ আছে, যখনকার তখনই, বেশি দিন থাকে না। একথা যে ঠিক নয় তা তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণ করা যায়। সংস্কৃত অভিধানে চুটকি শব্দ নেই, কিন্তু ওবস্তু যে সংস্কৃতসাহিত্যে আছে, সেকথা শাস্ত্রীমহাশয়ই আমাদের বলে দিয়েছেন। তাঁর মতে কালিদাস ও ভবভূতির পর চুটকি আরম্ভ হইয়াছিল; কেননা, শতক দশক অষ্টক সপ্তশতী এইসব তো চুটকিসংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তথাস্তু। শাস্ত্রীমহাশয়ের বর্ণিত সংস্কৃত চুটকির দুটি-একটি নমুনার সাহায্যেই দেখানো যেতে পারে যে, আর্যযুগেও চুটকি কাব্যাচাৰ্যদিগের নিকট অতি উপাদেয় ও মহা বস্তু বলেই প্রতিপন্ন হত। ভর্তৃহরির শতক-তিনটি সকলের নিকটই সপরিচিত, এবং ‘গাঁথা-সপ্তশতী’ও বাংলাদেশে একেবারে অপরিচিত নয়। ভর্তৃহরি ভবভূতির পূর্ববর্তী কবি; কেননা, জনরব এই যে তিনি কালিদাসের ভ্রাতা, এবং ইতিহাসের অভাবে কিংবদন্তীই প্রামাণ্য। সে যাই হোক, গাঁথা-সপ্তশতী’ যে কালিদাসের জন্মের অন্তত দু-তিন শ বছর পূর্বে সংগৃহীত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তাহলে দাঁড়াল এই যে, আগে আসে চুটকি তার পর আসে মহাকাব্য এবং মহানাটক। অভিব্যক্তির নৈসর্গিক নিয়মই এই যে, এ জগতে সব জিনিসই ছোট থেকে ক্রমে বড় হয়। সাহিত্যও ঐ একই নিয়মের অধীন। তার পর পূর্বোক্ত শতকত্রয় এবং পূর্বোক্ত সপ্তশতী যখনকার তখনকারই নয়, চিরদিনকারই। এ মত আমার নয়, বাণভট্টের। গাঁথাসপ্তশতী শুধু চুটকি নয় একেবারে প্রাকৃত-চুটকি, তথাপি শ্রীহর্ষকারের মতে
‘অবিনাশিনমগ্ৰাম্যমকরোৎসাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধ জাতিভিঃ কোশং রঙ্গৈরিব সুভাষিতৈঃ॥
তারপর ভর্তৃহরি যে একন’র পান্না এক-ন’র চুনি এবং এক-ন’র নীলা–এই তিন-ন’র রত্নমালা সরস্বতীর কণ্ঠে পরিয়ে গেছেন, তার প্রতি-রত্নটি যে বিশুদ্ধজাতীয় এবং অবিনাশী, তার আর সন্দেহ নেই। যাবচ্চন্দ্রদিবাকর এই তিন শত বর্ণোজ্জল লোক সরস্বতীর মন্দির অহর্নিশি আলোকিত করে রাখবে।
আসল কথা, চুটকি যদি হয় হয়, তাহলে কাব্যের চুটকিত্ব তার আকারের উপর নয় তার প্রকারে অথবা বিকারের উপর নির্ভর করে, নচেৎ সমগ্ৰ সংস্কৃত কাব্যকে চুটকি বলতে হয়। কেননা, সংস্কৃতভাষায় চার ছত্রের বেশি কবিতা নেই কাব্যেও নয় নাটকেও নয়। শুধু কাব্য কেন, হাতে-বহরে বেদও চুটকির অন্তর্ভূত হয়ে পড়ে। শাস্ত্রমহাশয় বলেন যে, বাঙালি-ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান ব’লে বেদাভ্যাস করেন না। কর্ণবেধের জন্য যতটুকু বেদ দরকার, ততটুকুই এদেশে ব্রাহ্মণসন্তানের করায়ত্ত। অথচ বাঙালি বেদপাঠ না করেও একথা জানে যে, ঋক হচ্ছে ছোটকবিতা এবং সাম গান। সুতরাং আমরা যখন ছোটকবিতা ও গান রচনা কবি, তখন আমরা ভারতবর্ষের কাব্যরচনার সনাতন রীতিই অনুসরণ করি।।
শাস্ত্রীমহাশয় মুখে যাই বলুন, কাজে তিনি চুটকিরই পক্ষপাতী। তিনি আজীবন চুটকিতেই গলা সেধেছেন, চুটকিতেই হাত তৈরি করেছেন, সুতরাং কি লেখায়, কি বক্তৃতায়, আমরা তাঁর এই অভ্যস্ত বিদ্যারই পরিচয় পাই। তিনি বাঙালির যে বিংশপর্ব মহাগৌরব রচনা করেছেন, তা ঐতিহাসিক চুটকি বই আর কিছুই নয়; অন্তত সে রচনাকে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অন্য কোননা নামে অভিহিত করবেন না।
একথা নিশ্চিত যে, তিনি সরকারমহাশয়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন নি, সম্ভবত এই বিবাসে যে, বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি অনুসারে আবিষ্কৃত সত্য বাঙালির পক্ষে পুষ্টিকর হতে পারে, কিন্তু রুচিকর হবে না। সরকারমহাশয় বলেন যে, এদেশের ইতিহাসের সত্য যতই অপ্রিয় হোক বাঙালিকে তা বলতেও হবে, শুনতেও হবে। অপরপক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের উদ্দেশ্য তাঁর রচনা লোকের মুখরোচক করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তিনি নানারকম সত্য ও কল্পনা একসঙ্গে মিলিয়ে ঐতিহাসিক সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ রচনায় যে মাল আছে, তাও মশলা থেকে পথক করে নেওয়া যায় না। শাস্ত্রীমহাশয়ের কথিত বাংলার পারাবত্তের কোনো ভিত্তি আছে কি না বলা কঠিন। তবে এ ইতিহাসের যে গোড়াপত্তন করা হয় নি, সেবিষয়ে আর দ্বিমত নেই। ইতিহাসের ছবি আঁকতে হলে প্রথমে ভূগোলের জমি করতে হয়। কোনোএকটি দেশের সীমার মধ্যে কালকে আবদ্ধ না করতে পারলে সে-কালের পরিচয় দেওয়া যায় না। অসীম আকাশের জিওগ্রাফি নেই, অনন্ত কালেরও হিস্টরি নেই। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় সেকালের বাঙালির পরিচয় দিতে গিয়ে সেকালের বাংলার পরিচয় দেন নি, ফলে গৌরবটা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে আমাদের কি অপরের প্রাপ্য এবিষয়েও সন্দেহ থেকে যায়। শাস্ত্রীমহাশয়ের শক্ত হাতে পড়ে দেখতে পাচ্ছি অঙ্গ ভয়ে বঙ্গের ভিতর সেধিয়েছে; কেননা, যে ‘হস্ত্যায়বেদ’ আমাদের সর্বপ্রথম গৌরব, সে শাস্ত্র অঙ্গরাজ্যে রচিত হয়েছিল। বাংলার লম্বাচৌড়া অতীতের গণবর্ণনা করতে হলে বাংলাদেশটাকেও একটু লম্বাচৌড়া করে নিতে হয়, সম্ভবত সেইজন্য শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের পূর্বপুরুষদের হয়ে অঙ্গকেও বেদখল করে বসেছেন। তাই যদি হয়, তাহলে বরেন্দ্রভূমিকে ছেটে দেওয়া হল কেন। শুনতে পাই, বাংলার অসংখ্য প্রত্নরাশি বরেন্দ্রভূমি নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে। বাংলার পূর্বগৌরবের পরিচয় দিতে গিয়ে বাংলার যে ভূমি সবচেয়ে প্রত্নগর্ভা, সে প্রদেশের নাম পর্যন্ত উল্লেখ না করবার কারণ কি। যদি এই হয় যে, পূর্বে উত্তরবঙ্গের আদৌ কোনো অস্তিত্ব ছিল না, এবং থাকলেও সেদেশ বঙ্গের বহির্ভূত ছিল, তাহলে সেকথাটাও বলে দেওয়া উচিত। নচেৎ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমাদের মনে একটা ভুল ধারণা এমনি বদ্ধমূল করে দেবে যে, তার ‘আমল পরিবর্তন’ কোনো চুটকি ইতিহাসের দ্বারা সাধিত হবে না।
শাস্ত্রীমহাশয় যে তাম্রশাসনে শাসিত নন, তার প্রমাণ তিনি পাতায় পাতায় বলেন, ‘আমি বলি’ ‘আমার মতে’ এই সত্য। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারে না, অর্থাৎ এককথায় তা কাব্য; এবং যখন তা কাব্য, তখন তা যে চুটকি হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি।
শাস্ত্রীমহাশয়ের, দেখতে পাই, আর-একটি এই অভ্যাস আছে যে, তিনি নামের সাদশ্য থেকে পৃথক-পথক বস্তু এবং ব্যক্তির ঐক্য প্রমাণ করেন। একীকরণের এ পদ্ধতি অবশ্য বৈজ্ঞানিক নয়। কৃষ্ট এবং খষ্ট, এ দুটি নামের যথেষ্ট সাদশ্য থাকলেও ও দুটি অবতারের প্রভেদ শুধু বর্ণগত নয়, বগগতও বটে। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয়ের অবলম্বিত পদ্ধতির এই একটি মহাগুণ যে, ঐ উপায়ে অনেক পর্বগৌরব আমাদের হাতে আসে, যা বৈজ্ঞানিক হিসেবে ন্যায়ত অপরের প্রাপ্য। কিন্তু উক্ত উপায়ে অতীতকে হস্তান্তর করার ভিতর বিপদও আছে। একদিকে যেমন গৌরব আসে, অপরদিকে তেমনি অগৌরবও আসতে পারে। অগৌরব শুধু যে আসতে পারে তাই নয়, বস্তুত এসেছে।
স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয় ‘ঐতরেয় আরণ্যক’ হতে এই সত্য উদ্ধার করেছেন যে, প্রাচীন আর্যেরা বাঙালিজাতিকে পাখি বলে গালি দিতেন। সে বচনটি এই–
‘বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা’
প্রথম-পরিচয়ে আর্যেরা যে বাঙালিজাতির সম্বন্ধে অনেক অকথা কুকথা বলেন, তার পরিচয় আমরা এ যুগেও পেয়েছি, vide Macaulay। সুতরাং প্রাচীন আর্যেরাও যে প্রথম-পরিচয়ে বাঙালিদের প্রতি নানারূপ কটু প্রয়োগ করেছিলেন, একথা সহজেই বিশ্বাস হয়। তবে এক্ষেত্রে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, যদি গালি দেওয়াই তাঁদের অভিপ্রায় ছিল, তাহলে আর্যেরা আমাদের পাখি বললেন কেন। পাখি বলে গাল দেবার প্রথা তো কোনো সভ্যসমাজে প্রচলিত দেখা যায় না। বরং বলবল’ ‘ময়না’ প্রভৃতি এদেশে আদরের ডাক বলেই গণ্য। এবং ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হলে আমরা তাকে ‘ঘুঘু’-উপাধিদানে সম্মানিত করি। অপমান করবার উদ্দেশ্যে মানুষকে যেসব প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে, তারা প্রায়শই ভূচর এবং চতুষ্পদ, দ্বিপদ এবং খেচর নয়। পাখি বলে নিন্দা করবার একটিমাত্র শাস্ত্রীয় উদাহরণ আমার জানা আছে। বাণভট্ট তাঁর সমসাময়িক কুকবিদের কোকিল বলে ভৎসনা করেছেন; কেননা, তারা বাচাল কামকারী এবং তাদের দৃষ্টি রাগাধিষ্ঠিত’—অর্থাৎ তাদের চক্ষু, রক্তবর্ণ। গাল হিসেবে এ যে যথেষ্ট হল না— সেকথা বাণভট্টও বুঝেছিলেন; কেননা, পরবর্তী শ্লোকেই তিনি বলেছেন যে, কুকুরের মত কবি ঘরে-ঘরে অসংখ্য মেলে, কিন্তু শরভের মত কবি মেলাই দুর্ঘট। এস্থলে কবিকে প্রশংসাচ্ছলে কেন শরভ বলা হল, একথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তার উত্তর, শরভ জানোয়ার হলেও চতুষ্পদ নয়, অষ্টপদ; এবং ‘তার অতিরিক্ত চারখানি পা ভূচর নয়, খেচর।
এইসব কারণে, কেবলমাত্র শব্দের সাদশ্যে থেকে এ অনুমান করা সংগত হবে না যে, আর্যঋষিরা অপর এত কড়াকড়া গাল থাকতে আমাদের পূর্বপুরুষদের কেবলমাত্র পাখি বলে গাল দিয়েছেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আমাদের সঙ্গে মাগধ এবং চের জাতিও এ গালির ভাগ পেয়েছে। কেননা, তাঁর মতে বঙ্গ হচ্ছে বাঙালি, বগধা হচ্ছে মগধা এবং চেরপাদা হচ্ছে চের নামক অসভ্য জাতি। ‘চেরপাদা’ যে কি করে ‘চের’তে দাঁড়াল, বোঝা কঠিন। বাক্যের পদচ্ছেদের অর্থ পা কেটে ফেলা নয়। অথচ শাস্ত্রীমহাশয় ‘চেরপাদা’র পা-দুখানি কেটে ফেলেই ‘চের’ খাড়া করেছেন।
‘বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা’— এইযুক্তপদের, শুনতে পাই, সেকেলে পণ্ডিতেরা এইরূপ পদচ্ছেদ করেন–
বঙ্গা+অবগধাঃ+চ+ইরপাদা
ইরপাদা অর্থে সাপ। তাহলে দাঁড়াল এই যে, বাঙালি ও বেহারিকে প্রথমে পাখি এবং পরে সাপ বলা হয়েছে। উক্ত বৈদিক নিন্দার ভাগ আমি বেহারিদের দিতে পারি নে। অবগধা মানে যে মাগধ, এর কোনো প্রমাণ নেই। অতএব শাস্ত্রীমহাশয় যেমন ‘চেরপাদা’র শেষ দুই বর্ণ ছেটে দিয়ে ‘চের’ লাভ করেছেন, আমিও তেমনি ‘অবগধা’ শব্দের প্রথম দুটি বর্ণ বাদ দিয়ে পাই ‘গধা’। এইরূপ বর্ণবিচ্ছেদের ফলে উক্ত বচনের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আর্যঋষিদের মতে বাঙালি আদিতে পক্ষী, অন্তে সর্প এবং ইতিমধ্যে গর্দভ।
‘অবগধা’কে ‘গধা’য় রুপান্তরিত করা সম্বন্ধে কেউ-কেউ এই আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, সেকালে যে গাধা ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। শাস্ত্রীমহাশয় বাঙালির প্রথম গৌরবের কারণ দেখিয়েছেন যে, পরাকালে বাংলায় হাতি ছিল, কিন্তু বাঙালির দ্বিতীয় গৌরবের এ কারণ দেখান নি যে, সেকালে এদেশে গাধাও ছিল। কিন্তু গাধা যে ছিল, এ অনুমান করা অসংগত হবে না। কেননা, যদি সেকালে গাধা না থাকত তো একালে এদেশে এত গাধা এল কোথা থেকে। ঘোড়া যে বিদেশ থেকে এসেছে, তার পরিচয় ঘোড়ার নামেই পাওয়া যায়; যথা পগেয়া ভুটিয়া তাজি আরবি ইত্যাদি। কিন্তু গর্দভদের এরূপ কোনো নামরূপের প্রভেদ দেখা যায় না। এবং ও জাতি যে যে-কোনো অর্বাচীন যুগে বঙ্গদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তারও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, রাসভকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এদেশে এখনও আছে, পূর্বেও ছিল। তবে একমাত্র নামের সাদশ্য থেকে এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে যে, আর্যঋষিরা পুরাকালের বাঙালিদের এরূপ তিরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন। সংস্কৃতভাষায় ‘বঙ্গ’ শব্দের অর্থ বক্ষ। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আরণ্যকশাস্ত্রে বক্ষ পক্ষী সর্প প্রভৃতি আরণ্য জীবজন্তুরই উল্লেখ করা হয়েছে, বাঙালির নামও করা হয় নি। অতএব আমাদের অতীত অতি গৌরবেরও বস্তু নয়, অতি অগৌরবেরও বস্তু নয়।।
আর-একটি কথা। হীরেন্দ্রবাবু দর্শন-শব্দের, এবং যোগেশবাবু বিজ্ঞানশব্দের নিরুক্তের আলোচনা করেছেন, কিন্তু যদুবাবু ইতিহাসের নিরুক্ত সম্বন্ধে নীরব। ইতিহাস-শব্দ সম্ভবত হস্ ধাতু হতে উৎপন্ন, অন্তত শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস যে হাস্যরসের উদ্রেক করে, সেবিষয়ে আর-কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি, আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, শাস্ত্রীমহাশয় পুরাতত্ত্বের ছলে আত্মশ্লাঘাপরায়ণ বাঙালিজাতির সঙ্গে একটি মস্ত রসিকতা করেছেন।
জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
জয়দেব
একখানি সাহিত্যগ্রন্থকে দুই রকম ভাবে আলোচনা করা যায় : প্রথমতঃ, কাব্যস্বরূপে; দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারের উপায় স্বরূপে।
প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিলে আমরা কেবলমাত্র তাঁহার দেশকালনিরপেক্ষ কাব্য হিসাবে দোষগুণবিচারে সমর্থ হই।
দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিলে আমরা তাহা যে নির্দিষ্ট সময়ে যে দেশে রচিত হইয়াছিল, সেই দেশের তৎসাময়িক অবস্থাসকলের আলোচনাঘারা তাঁহার তর্দেশীয় অন্যান্য কাব্যসকলের সহিত কি সম্বন্ধ এবং তাঁহার দোষ ও গুণ কোন কোন বিশেষ কারণপ্রসূত, এইসকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি।
কাব্যের দোষগুণবিচার করাই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক প্রথায় আলোচনা উক্ত বিচারের সহায়তাসাধন করে মাত্র। কিন্তু এই উভয় পদ্ধতির মিলিত সাহায্যেই যথার্থ সমালোচনা করা যায়।।
দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সহিত জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের কি সম্বন্ধ তাহা আমার নিকট অবিদিত; এবং ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধেও আমার পরিমিত জ্ঞান, জয়দেবের সময়ে, অর্থাৎ বঙ্গীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে, বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাদির সম্যক্ নির্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুতরাং উপস্থিত প্রবন্ধে আমাকে জয়দেবের গ্রন্থ কেবলমাত্র কাব্য হিসাবে বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। আর-একটি কথা, শুনিতে পাই গীতগোবিন্দের নাকি একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে; জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিগুঢ় মিলনের বিষয়ই নাকি রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোনো পরিচয় নাই। জয়দেব তাঁহার কাব্যে যেসকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহার সহজ ও প্রচলিত অর্থ অনুসারে যতটা বুঝা যায় তাহাই বুঝিয়াছি, কোনো নিগূঢ় অর্থ উদ্ভাবন করিতে পারি নাই। আমার কাছে কৃষ্ণ ও রাধাকে আমাদেরই মত রক্তমাংসে-গঠিত মানুষ বলিয়া বোধ হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রেমকেও স্ত্রীপুরুষঘটিত সাধারণ মানবপ্রেম বলিয়াই বুঝিয়াছি। যদি যথার্থই একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক ভাব কাব্যখানির প্রাণস্বরূপ হয় তাহা হইলে আমি উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা একান্ত অর্থশূন্য। সূচনাস্বরূপ এই অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখমাত্র করিয়া আমি আসল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।
২.
রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক দুই-চারিটি ঘটনা লইয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন।
একদিন কৃষ্ণ গোপিনীগণ সমভিব্যাহারে যমুনাতীরে বসন্তবিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাধা বেশভূষা করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে তথায় আসিয়া উক্ত ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণও একান্ত অপ্রতিভ হইয়া মৌনভাব ধারণ করিয়া রহিলেন এবং রাধাকে গমন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টামাত্র করিতেও সাহসী হইলেন না। কিন্তু, রাধা চলিয়া গেলেন দেখিয়া তিনি গোপবধূদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোনো-এক নিভৃত কুঞ্জবনে আশ্রয় লইয়া মনোদুঃখে রাধার কথা ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে রাধা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ-কৃত পূর্ববিহারস্মরণে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে আনয়নার্থ তাঁহার নিকট সখী প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ সখীকে বলিলেন, ‘আমি যাইতে পারিব না, তাহাকে আসিতে বল।‘ তার পর সখীর রাধার নিকট প্রত্যাগমন এবং কৃষ্ণের প্রার্থনানুযায়ী রাধাকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইবার চেষ্টা। কিন্তু রাধা ইচ্ছা থাকিলেও বিরহজনিত শারীরিক ক্লান্তি হেতু স্থান পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। সখী অগত্যা আবার কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণ এবার রাধার সকাশে. স্বয়ং যাইতে রাজি। সখী ছুটিয়া আসিয়া রাধাকে সুসংবাদ জানাইলে রাধা বাসকসজ্জা হইয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কথা রাখিতে পারিলেন না। কাজেই রাধা ঠাহরাইলেন যে, কৃষ্ণ অন্য-কোনো রমণীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সহিত জমিয়া গিয়াছেন। উক্ত রমণীর সহিত কৃষ্ণ কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, সেইসকল কথা রাধা কল্পনায় অনুভব করিয়া সেই ভাগ্যবতীর তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত হতভাগিনী মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাত্রি এইরূপেই কাটিয়া গেল। প্রত্যুষে কৃষ্ণ অন্য রমণীর ভোগচিহ্নসকল শরীরে ধারণ করিয়া রাধার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাধা কৃষ্ণকে কিরূপ ভাষায় সম্ভাষণ করিলেন, তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক নাই। কৃষ্ণ নিজের দোষক্ষালনের কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না, কারণ সে চেষ্টা নিষ্ফল। অধরের কজ্জল, কপোলের সিন্দুর, বক্ষঃস্থ যাবকরঞ্জিত পদচিহ্ন— এসকল কোথা হইতে আসিল। তাহার নাহয় একটি বাজে কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরিধানের নীল শাড়ী সম্বন্ধে তো আর কোনোরূপ মিথ্যা কৈফিয়ত খাটে না। রাধা কথা শেষ করিয়া দুর্জয় মান করিয়া বসিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে কি মান টিকে? তিনি মনোমত কথায়, রাধার প্রীতিসাধন করিলেন, রাধা কৃষ্ণের উপরে যে আড়ি করিয়াছিলেন তাহা ভাবে পরিণত হইল। এই তো গেল প্রভাতসময়ের ঘটনা। যোগেযাগে দিনটিও কাটিয়া গেল। দিনান্তে অভিসারিকা রাধা কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উভয়ের মিলন হইল। মিলনান্তর সম্ভোগ, সম্ভোগান্তর কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার বেশবিন্যাসের সঙ্গেসঙ্গেই গ্রন্থের সমাপ্তি।
দেখা যাইতেছে, এ কাব্যের মুখ্য বর্ণিত বিষয় রাধাকৃষ্ণের রূপ; তাঁহাদের পরস্পরের বিরহে পরস্পরের দুঃখপ্রকাশ; মিলিত হইলে পরস্পরে কথোপকথন অর্থাৎ কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের দেহের বর্ণনা ও তাঁহাদের মনোগত প্রেমভাবের বর্ণনা। এ ছাড়া আনুষঙ্গিকরূপে যমুনাতীর কুঞ্জবন বসন্তকাল রাধার সখী ও অন্যান্য গোপিনীগণের কথাও বলা হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় ও ঈশ্বরের বন্দনা বাদ দিলে দেখা যায়, রাধা ও কৃষ্ণের কেলি ব্যতীত স্বর্গমর্ত্যপাতালের অন্য কোনো বিষয়, কোনোরূপ ধর্মনৈতিক কিংবা নৈতিক মতামত ইত্যাদি কিছুই গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করে নাই। জয়দেবের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো চিন্তা ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ কবির ক্ষমতার পরিসর যত সংক্ষিপ্ত হয় ও তাঁহার কল্পনা যত সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বদ্ধ থাকে, ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন সমালোচকের পক্ষে সমালোচনা করাটা ততই সহজসাধ্য হইয়া উঠে। আমি এখন জয়দেবে যাহা নাই তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহাতে যাহা আছে তাঁহার বিষয়ই আলোচনা করিব। জয়দেবের কবিত্বশক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্বে আমি তাঁহার বর্ণিত প্রেম কিরূপ ও তাঁহার বর্ণিত স্ত্রীপুরুষের রূপই বা কিরূপ, তাহাই যথার্থরূপে নিরূপণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি।
মনের ভাবের প্রকাশ কথায় ও কার্যে। সাধারণ গোপিনীগণ, রাধা ও কৃষ্ণ, ইহারা প্রেম শব্দের অর্থে কি বুঝেন তাহা তাঁহাদের কথায় ও কার্যে বিশেষরূপে বুঝা যায়। গোপিনীগুণ কৃষ্ণের কামোদ্দীপ্ত মুখের উপরে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া কানে-কানে কথা কহিবার ছলে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া, পীনপয়োধরভারভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, ‘কেলিকলাকুতুকেন’ কুঞ্জবনে প্রবেশের নিমিত্ত তাঁহার পরিহিত দুকূল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি স্বীয় প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন।
রাধা কৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়া সখীকে বলিলেন–
সখি হে কেশিমথনমুদারম্
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্।
তাঁহার পর কৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে কৃষ্ণ কি করিবেন এবং তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইবে, রাধা সে-বিষয়ে সখীকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতাটি ইচ্ছা সত্ত্বেও এ সভায় আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে পারিলাম না। নিজেরা পড়িয়া দেখিলেই তাহাতে রাধা বিরহ ও মিলন কিভাবে দেখেন তাহা অতি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।
সখী কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহ-অবস্থা জানাইয়া বলিতেছেন, রাধা–
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্।
আরো নানা কথা বলিলেন, ফলে দাঁড়াইল রাধার অবস্থা অতি শোচনীয়; তিনি অতিশয় উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত, রক্ষা পাওয়া ভার; রোগের কারণ কৃষ্ণের বিরহ। রোগ অতি কঠিন হইলেও কৃষ্ণের দ্বারা অতি সহজেই তাঁহার প্রশমন হইতে পারে। সখী কৃষ্ণকে বলিলেন, এ রোগ–
ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্ৰসাধ্যাম্।
আর কৃষ্ণ? তিনিও কথা এবং ব্যবহারে তাঁহার মনোভাব নিঃসন্দেহরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র চুম্বন আলিঙ্গন রমণ ইত্যাদির দ্বারা গোপিনীগণের প্রতি তাঁহার অন্তরের ভালোবাসা প্রকাশ করেন। সখীদ্বারা রাধাকে বলিয়া পাঠান যে, যাও শ্ৰীমতীকে গিয়া বল–
ভূয়স্ত্বৎকুচকুম্ভনিৰ্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি।
কৃষ্ণ রাধার দুর্জয় মান ভঞ্জনার্থ যেসকল চাটুবচন প্রয়োগ করেন তাহাতেও ঐ একটি ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি সকলেই যে-ভাবে মত্ত সে-ভাবের নাম সংস্কৃতে ঠিক প্রেম নহে। জয়দেব-বর্ণিত প্রেমের উৎপত্তি দেহজ আকাঙ্ক্ষা হইতে, তাঁহার পরিণতি দেহের মিলনে, তাঁহার উদ্দেশ্য দেহের ভোগজনিত সুখলাভ; তাঁহার নিকট বিরহের অর্থ প্রণয়ীপ্রণয়িনীর দেহের বিচ্ছেদজনিত শারীরিক কষ্ট।
গীতগোবিন্দে আসল ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই, কেবলমাত্র কামের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই, শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার। যে রমণীর মনে প্রেম নাই, যাহার হৃদয় নাই, কেবলমাত্র দেহ আছে— তাঁহার স্ত্রীসুলভ লজ্জা নম্রতা ইত্যাদি মানসিক সৌন্দর্যের বিশেষ অভাব থাকিবার কথা; রাধিকাপ্রমুখ গোপযুবতীদিগের এই নির্লজ্জতার পরিচয় তাঁহাদের ব্যবহারে ও কথোপকথনে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করা যায়। রাধা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে ‘স্মরশরপরবশাকুত’ প্রিয়মুখ দেখিয়া নির্লজ্জভাবে উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন।
এই তো গেল প্রেমের কথা, এখন শারীরিক সৌন্দর্যের কথা পাড়া যাউক। শারীরিক সৌন্দর্য তিনটি বিভিন্ন উপকরণে গঠিত–
১ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন বা আকৃতি
২ বর্ণ।
৩ ভাব, অর্থাৎ আন্তরিক সৌন্দর্যের বাহবিকাশ। জয়দেবের নায়কনায়িকা যখন সর্বাংশে আন্তরিক সৌন্দর্যবঞ্চিত তখন অবশ্য তাঁহাদের শরীরে ভাবের সৌন্দর্যের দেখা পাওয়া অসম্ভব।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের পরিমাণ সামঞ্জস্য ও বর্ণ এসকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ইহাতে কোনোরূপ ভোগের ভাব সংলিপ্ত নহে। যে সৌন্দর্য চোখে দেখা যায়, তাঁহার কেবল মানসিক উপভোগই সম্ভব; তাহা হইতে. যে সুখ লাভ করা যায় তাহা কেবলমাত্র মানসিক আনন্দ; তাহাতে দেহের কোনোরূপ লাভলোকসান নাই। কিন্তু স্পর্শ করিয়া যে সুখ তাহা চৌদ্দআনা দৈহিক, সুতরাং জয়দেবের নিকট আমরা আকৃতি ও বর্ণের সৌন্দর্য অপেক্ষা শারীরিক কোমলতা ও স্পর্শযোগ্যতা ইত্যাদির অধিক বর্ণনা প্রত্যাশা করিতে পারি এবং জয়দেব এ বিষয়ে আমাদিগকে নিরাশ করেন না। মুখশ্রীর প্রধান উপকরণ ভাব, গঠন ও বর্ণের সৌন্দর্য। তাই জয়দেব মুখশ্রীবর্ণনা দুই কথায় করিয়াছেন, যে দুইটি কথা বলেন তাহাও খানিকটা যেন না বলিলে নয় বলিয়া।
গীতগোবিন্দের মুখ্য বিষয়টি কি, তাহা আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা আপনাদিগকে এতক্ষণ ধরিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, এখন আমি তাঁহার কাব্যাংশের দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।
৩.
কোনো-একটি বিশেষ রচনা কাব্য কি না, ও যদি কাব্য হয় তাহা হইলে কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ কিংবা নিকৃষ্ট এসকল বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে আগে কাব্য কাহাকে বলে সে বিষয়ে কতকটা পরিমাণে পরিষ্কাররূপ ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা প্রায় সকলেই সচরাচর কবিতা-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি এবং আমাদের সকলেরই মনে কাব্য যে কি পদার্থ সে বিষয়ে একটা ধারণাও আছে, সেটি যে কি তাহা ঠিক প্রকাশ করিয়া বলা অত্যন্ত কঠিন। কোনো-একটি ক্ষুদ্র সংজ্ঞার ভিতর পৃথিবীর যাবতীয় কবিতাপুস্তক প্রবেশ করানো যায় না। দুই-চারি কথায় কোনো কাব্যের সমস্ত গুণের বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু সকল কাব্যের ভিতর যেটি সাধারণ অংশ তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে তাহা যে কি, সে বিষয়ে একটি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। আমার বিবেচনায় আমাদের দেশে প্রচলিত ‘কাব্য রসাত্মক বাক্য’(১) কাব্যের এই সংজ্ঞায়, সকল কাব্যের ভিতর যেটি সাধারণ অংশ, অর্থাৎ যাহার অভাবে কোনো রচনা কাব্য হইতে পারে না, সেইটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই অল্পসংখ্যক কথা কয়েকটির মধ্যে কি ভাব নিহিত আছে তাহা খুলিয়া বুঝাইয়া দিলে বোধ হয় আপনারাও আমার কথা কতক পরিমাণে গ্রাহ্য করিবেন।
‘রসাত্মক বাক্য’–এই কথা কয়েকটির যথার্থ অর্থ বুঝিতে হইলে রস আত্মা ও বাক্য এই শব্দগুলির অর্থ জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ, বাক্য এই শব্দ লইয়াই আরম্ভ করা যাউক; আমরা দেখিতে পাই বাক্যের দুইটি অংশ আছে। প্রথম, অর্থ; দ্বিতীয়, শব্দ। প্রথমাংশ মানসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য; দ্বিতীয়াংশ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যে শব্দ কানে শুনিয়া অন্তরে তাঁহার অর্থ গ্রহণ করি তাহাই বাক্য।
বাক্যের বিষয় মানুষের মনোভাব।
বাক্যের উদ্দেশ্য তাহা প্রকাশ করা এবং উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের উপায় শব্দ। সুতরাং বাক্য রসাত্মক হইতে হইলে, প্রথমতঃ, ভাব রসাত্মক হওয়া আবশ্যক; দ্বিতীয়ত, শব্দ রসাত্মক হওয়া আবশ্যক; তৃতীয়তঃ, এরূপভাবে প্রকাশ করা কর্তব্য যাহাতে রসাত্মক ভাব রসাত্মক শব্দের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইতে পারে।
শব্দের রস কি? অবশ্য শ্রুতিমধুরতা; যেমন সংগীতে একটি সুর আরএকটি সুরের সহিত মিশ্রিত হইয়া অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়, সেইরূপ একটি শব্দ আর-একটি শব্দের সংস্পর্শে অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়। কানে শুনিতে ভালো লাগিবার জন্য শব্দবিন্যাসের পারিপাট্য হইতে ছন্দের উৎপত্তি। ভাষা ছন্দোবদ্ধ হইলে যত শুনিতে ভালো লাগে, ছন্দব্যতিরেকে ততদূর মিষ্টি লাগে না। সুতরাং কবির ভাষা ছন্দোযুক্ত। পদ্যে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান প্রথম rhyme, দ্বিতীয় rhythm। এই দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টিই ছন্দের প্রাণস্বরূপ; rlyne না থাকিলেও ছন্দ হয় কিন্তু rhythm না থাকিলে চলে না; rhyme ও rhythm উভয়েই সমভাবে বর্তমান থাকিলেই ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণাবয়ব হয়। সুতরাং যে কবির রচনায় rhyme এবং rhythm যত বহুলপরিমাণে থাকিবে ততই তাঁহার শব্দের রস বেশি হইবে।
যে ভাব মনে সুন্দর ভাবের উদ্রেক করে, আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ আনন্দে পরিপ্লুত করে তাহাই রসাত্মক ভাব। যেমন ফুল, সুগঠিত প্রস্তরমূর্তি, পূর্ণিমারজনী ইত্যাদি আমাদের দেখিতে ভালো লাগে কিন্তু কেন লাগে তাঁহার কোনো কারণ নির্দেশ করা যায় না, সেইরূপ মানবমনের প্রেম ভক্তি স্নেহ, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষাজনিত বিষাদ, জগতের আদি অন্ত উদ্দেশ্য ইত্যাদি রহস্যপূর্ণ বিষয়ের চিন্তাজনিত মনের আবেগ, বিস্ময়াদি ভাবসকল সহজেই আমাদের ভালো লাগে; কিন্তু কেন যে ভালো লাগে তাঁহার কোনো কারণ নির্দেশ করা যায় না। উক্ত প্রকার রসাত্মক ভাবসকলই কাব্যের মুখ্য বিষয়। এইসকল ভাবের ভিতর যে মাধুর্য আছে তাহাই প্রকাশ করা এবং আমাদের মনে এইসকল ভাব উদ্রেক করিয়া আনন্দ প্রদান করাই কবিতার উদ্দেশ্য এবং যে কবি সেই উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য হয়েন তিনিই যথার্থ শ্রেষ্ঠ কবি। যদিও সুন্দর ভাব লইয়াই কবির কারবার, তথাপি পৃথিবীর কোনো সুন্দর জিনিস একেবারে তাঁহার আয়ত্তের বহিভূত নয়। কি বাহিক, কি মানসিক যতপ্রকার সৌন্দর্য আছে সকলেরই ভিতর একটা বিশেষ মিল আছে। চিত্রকরের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি দ্বারা লোকের মানসিক তৃপ্তি সাধন, কিন্তু তিনি তাঁহার চিত্রে বাহ্যিক সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া ভাবের সৌন্দর্য, ফুটাইয়া তুলিতে পারেন; কবির পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। ভাবের সৌন্দর্য প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইলেও তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের বর্ণনাতেও ক্ষান্ত নহেন, বরং যে কবি নিজের রচনায় রূপজ ভাবজ নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ সৌন্দর্যের একত্ৰ মিলন করিতে পারেন তিনিই তত উচ্চদরের কবি বলিয়া গণ্য হয়েন। কিন্তু যেমন একটি চিত্রকরের পক্ষে চিত্রে ভাবের সৌন্দর্য প্রকটিত করিতে হইলে প্রথমতঃ চিত্রটিকে সুন্দর করিয়া আঁকিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ যাহাতে তাঁহার ভাব পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয় সেইরূপ করিয়া আঁকিতে হইবে; কবির পক্ষেও ঠিক সেইরূপ কোনো-একটি বিষয় কাব্যভুক্ত করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে ভাবের সৌন্দর্যের সহিত লিপ্ত করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইবে।
আমি ভাষা ও ভাব পৃথক করিয়া আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক কবির নিকট ভাষা ও ভাবের ভিতর কোনো প্রভেদ নাই। কবিতার ভাষা ও ভাব পরস্পরের উপর পরস্পর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ভাব মন্দ হইলে কবিতার ভাষা কখনোই সুন্দর হইতে পারে না, এবং ভাষা কদর্য হইলে ভাবও সম্পূর্ণরূপ কবিত্বপূর্ণ হইতে পারে না। কবিতার ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ, কিছুতেই তাহা ভাব হইতে পৃথক করিতে পারা যায় না। একটি ভাব দুইপ্রকার ভাষায় ব্যক্ত হইলে অর্থ সম্বন্ধে অনেকটা বিভিন্ন হইয়া যায়। নিবিড় অন্ধকারকে কালিদাস বলিতেছেন ‘সূচিভেদ্যস্তমস্’, জয়দেব বলিতেছেন ‘অনল্পতিমির। এ দুয়ের মধ্যে কতটা প্রভেদ আপনারাই বুঝিতে পারিতেছেন।
যে অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা কবিতায় ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ একীকরণ সম্পন্ন হয় তাহাই কবিতার আত্মা। এই আত্মা আমাদের আত্মার ন্যায় রহস্যজড়িত। যেমন বৈজ্ঞানিকগুণ মানবদেহ খণ্ডখণ্ড করিয়া তাঁহার ভিতরকার আত্মাকে খুঁজিয়া পান না, সেইরূপ সমালোচকেরাও একখানি কাব্যের বিভিন্ন উপাদানসকল পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট করিলেও তাঁহাদের অন্তরস্থ আত্মাকে ধরিতে পারেন না। যাঁহারা ভাবের সহিত ভাষা যুক্ত করিয়া কবিতাকে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন তাঁহাদেরই কবিতার আত্মা আছে। কিন্তু যথার্থ কবিত্বশক্তিবিবর্জিত কোন ব্যক্তি যদি বহুল পরিশ্রম দ্বারা বিশেষরূপে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ভাব-সকলকে পরিপাটি জল ও ভাষা যুক্ত করেন তাহা হইলেও তাঁহার রচনা কাব্যশ্রেণীভুক্ত নয়। সৃষ্টি ও নির্মাণে যে প্রভেদ, কবিতা ও তাঁহার অনুকরণে রচিত প্রাণশূন্য ছন্দোবন্ধের সমষ্টিতে সেই প্রভেদ।
পূর্বে যাহা বলিলাম তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে দাঁড়ায় এই যে, যে রচনায় রসাত্মক ভাব সম্পূর্ণরূপ অনুরূপ ভাষায় প্রকাশিত তাহাকেই আমি কাব্য বলিয়া মানি। এখন দেখা যাউক কাব্য-বিষয়ে আমার মত অনুসারে বিচার করিলে জয়দেবের কাব্যজগতে স্থান কোথায়।
৪.
জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয়নির্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়াছেন; প্রেমের পরিবর্তে শৃঙ্গাররসকে কবিতার বর্ণিত বিষয়স্বরূপ স্থির করিয়াছেন, সেজন্য আমরা কখনো তাহাকে কালিদাসাদি কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। আমি আপাততঃ জয়দেব বিষয়টি কাব্যাকারে গঠিত করিয়া কিরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহাই বলিতেছি।
জয়দেবের কবিতাসকল প্রকৃতির শোভা, রাধাকৃষ্ণের রূপ এবং তাঁহাদের বিরহমিলন ইত্যাদি অবস্থার বর্ণনায় পূর্ণ; সুতরাং তাঁহার বর্ণনাবিষয়ে কৃতকার্যতা অনুসারে তাঁহার কবিত্বশক্তির স্বরূপ নির্ধারিত হইবে। কবিরা দুইরূপ প্রণালীতে বর্ণনা করিয়া থাকেন— প্রথম, স্পষ্ট এবং সহজভাবে, দ্বিতীয়, বর্ণিত বিষয় ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। উভয় উপায়ই প্রকৃষ্ট, এবং শ্রেষ্ঠ কবিরা উভয় প্রণালী অনুসারেই বর্ণনা করিয়া থাকেন। জয়দেব কেবলমাত্র প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্ণনার পারিপাট্য ও সৌন্দর্য উপমাদি অলংকারসকলের প্রয়োগ দ্বারা বিশেষরূপে সাধিত হয়। এ জগতের সকল পদার্থের মধ্যেই একটা মিল আছে। আমাদের সময়ে সময়ে কোনো-একটি পদার্থ কিংবা ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যেন আর অন্য একটি কি জিনিসে এইরূপ ভাব দেখিয়াছিলাম। পৃথক পৃথক পদার্থের ভিতরকার এই সাদৃশ্যের তুলনা হইতে উপমাদির উৎপত্তি।
উপমাদির দ্বারা দুইটি কার্য সিদ্ধ হয় : ১. ইহার দ্বারা একটি অস্পষ্ট ভাবকে স্পষ্ট করা যায়, ২. ইহার দ্বারা ভাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। ইহা ব্যতীত কোনো দুইটি ভাব বা পদার্থের ভিতর আমার অক্ষিত কোনোরূপ মিল কেহ দেখাইয়া দিলে মনে বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়। কবিতায় যেসকল উপমা ব্যবহৃত হয় তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য কোননা-একটি ভাবের উপমার সাহায্যে সৌন্দর্যবৃদ্ধি, এবং কেবলমাত্র উপমার যাথার্থ দ্বারা মনের তুষ্টিসাধন, সুতরাং জয়দেবের বর্ণনার যাথার্থ্য এবং সৌন্দর্য অনেকটা তাঁহার উপমাদি অলংকার প্রয়োগের শক্তিসাপেক্ষ।
জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনা নেহাত একঘেয়ে। তাঁহার বিরহীবিরহিণীদিগের নিকট যে বস্তু মনের সহজ অবস্থায় ভালো লাগিবার কথা তাহাই শুধু খারাপ লাগে। জয়দেব বিরহের ভাবের অন্য-কোনো অংশ ধরিতে পারেন নাই। কালিদাসের মেঘদূত-কাব্যে যক্ষস্ত্রীর যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে জয়দেবের বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাব এবং বিরহাবস্থার মধ্যে যে মধুর সৌন্দর্য আছে তাঁহার সম্পূর্ণ উল্লেখের অভাব–এই দুইটি ত্রুটি আমাদের নিকট স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।
জয়দেবের অভিসারবর্ণনায় কেবলমাত্র বেশভূষার বর্ণনাই দেখিতে পাই। তাহাতে অভিসারিকার মনের আবেগ, প্রেমের নিমিত্ত অবল। রমণীগুণ কিরূপে নানারূপ বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এসকল বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। এ বর্ণনাও নেহাত একঘেয়ে। তাঁহার বসন্তবর্ণনার প্রধান দোষ তাহাতে একটিও সম্পূর্ণ নুতন কথা দেখিতে পাই না। পূর্ববর্তী কবিরা যেসকল বসন্তবর্ণনা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার বসন্তবর্ণনার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। নূতনত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাতে আরো অনেক দোষ বাহির হইয়া পড়ে। তাঁহার সমস্ত বর্ণনাটিতে সমগ্র বসন্তের ভাব ফুটিয়া উঠে না। তিনি এ কথা ও কথা বলেন, কিন্তু তাঁহার ভিতর হইতে একটা কোনো বিশেষ ভাব খুব স্পষ্টরূপে দেখা যায় না।। কালিদাস অনেক স্থলে বসন্তবর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক স্থলেই তিনি একটিমাত্র শ্লোকে হয় বসন্তের সমগ্ৰভাব প্রকাশ করিয়াছেন, নয় একটিমাত্র চিত্রে সমস্ত বসন্ত আবদ্ধ করিয়াছেন—
দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং
স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ
সর্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে।।
জয়দেব বসন্তবর্ণনায় অনেকগুলি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে খুব একটা ভাবের মিল নাই। তিনি একটি শ্লোকের প্রথম চরণে বলিতেছেন যে ‘বসন্তে বিরহীগুণ বিলাপ করিতেছেন’; সেই শ্লোকের আর-একটি চরণে ‘অলিকুল কর্তৃক বকুলকলাপ অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ দুয়ের ভিতর যে কি স্বাভাবিক মিল তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাঁহার উদ্দেশ্য, বসন্তে যে মদন-রাজার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে। তাহাই বর্ণনা করা। কিন্তু কেবলমাত্র কোনো ফুলকে মদন-রাজার নখ এবং অন্য অপর আর-একটিকে বিরহীদিগের হৃদয়বিদারণের অস্ত্রস্বরূপ বলিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যথার্থ মদনবিকারের ভাব কিসে ফুটিয়া উঠে তাহা আমি কালিদাসের একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—
মধু দ্বিরেফঃ কুসুমেকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমান।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
উক্ত শ্লোকে কালিদাস মদনের নখ দূরে যাউক তাঁহার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, তথাপি প্রেমরসমত্ততার কি চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। সমগ্র ভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও জয়দেব এমন একটিমাত্রও শ্লোক রচনা করিতে পারেন নাই যাহাতে কোনো-একটি পদার্থের সজীব চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতিবর্ণনাতেও যেরূপ স্ত্রীপুরুষের রূপবর্ণনাতেও তিনি ঠিক সেইরূপ অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। কালিদাস
আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসে বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।
এই একটিমাত্র শ্লোকে সমগ্র উমাকে কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। জয়দেব এইরূপ দুই-চার কথায় একটি স্ত্রী কিংবা পুরুষের সমগ্র চিত্র বর্ণনা করিতে একান্ত অপারগ। তাঁহার বিশ্বাস পদ্মের স্যায় মুখ, তিলফুলের ন্যায় নাসিকা, ইন্দীবরের ন্যায় নয়ন এবং বান্ধুলির ন্যায় অধর–এইসকলের একটি সমষ্টি করিলেই সুন্দরীর মুখ নির্মাণ করা যায়। উক্ত বিশ্বাসে ভর করিয়া সুন্দর-কবি বিদ্যাকে একটি পদ্মের সহিত তিলফুল নীলোৎপল বান্ধুলিপুষ্প এবং কুকলিকা ইত্যাদি অতি কৌশলসহকারে সংযোজনা করিয়া যে অপূর্ব মূর্তি নির্মাণ করিয়া উপহার। স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন তাহা অবশ্য জয়দেবের নিকট তিলোত্তমার মুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। উক্ত প্রকার বিশ্বাসের উপর আমার কোনোই আক্রোশ নাই, যিনি ইচ্ছা করেন অনায়াসে তিনি ঐসকল ফুল জোড়াতাড়া দিয়া যখনতখন মনের সুখে সুন্দরীর রূপবর্ণনা করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন। কেবল এইটিমাত্র মনে রাখিলেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব যে, পদ্ধতি অনুসারে চলিলে মাথামুণ্ড কিছুই বর্ণনা করা যায় না।
তার পর জয়দেবের উপমার বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে জয়দেবের উপমাসকল প্রায়ই নেহাত পড়ে-পাওয়াগোছের। জয়দেবের পুর্বে সেইসকল উপমা শতসহস্রবার সংস্কৃতকবিগণ। কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। জয়দেব কাব্যজগতের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে তাহা কুড়াইয়া লইয়াছেন মাত্র। কাব্যজগতে না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করার প্রথাটা বিশেষরূপ প্রচলিত আছে এবং কোনো কবি যদ্যপি উক্ত উপায়ে। উপার্জিত দ্রব্যের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন তাহা হইলে তাহাকে লোকে কিছু-একটা বিশেষ দোষও দেয় না। নেহাত পরের দ্রব্য বলিয়া চেনা গেলেই আমরা রাগ করি এবং কবির উদ্দেশে কটুকাটব্যও ব্যবহার করি; কিন্তু যদি তাঁহার একটুমাত্রও রূপের পরিবর্তন দেখিতে পাই তাহা হইলেই ঠাণ্ডা থাকি। জয়দেব অনেক স্থলেই পরের উপমাদি লইয়া তাঁহার একটু-আধটু বদলাইয়া নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার এ বিষয়ে হাত বড় মন্দ সাফাই নহে; আবার অনেক স্থলে যেমনটি পাইয়াছেন অবিকল তেমনটি রাখিয়াছেন। এইরূপ উপমাদি পড়িয়া রাগ করি আর না করি, খুব যে খুশি হই তাহা নহে। যে কথা হাজারবার শুনিয়াছি তাহা আর কার শুনিতে ভালো লাগে। আমার তো পদ্মের মত মুখ ইত্যাদি কথা শুনিলেই মনটা একটু অন্যমনস্ক হয় এবং ঐরূপ উপমা বেশিক্ষণ পড়িতে হইলেই হাই উঠিতে আরম্ভ হয়, কারণ ওসব পুরানো কথায় মনে কোনো নির্দিষ্ট ভাব বা চিত্র আসে না। শুনিবামাত্রই মনে হয় ওসব তো অনেকদিনই শুনিয়াছি, আবার অনর্থক ও কথা কেন? ভরসা করি, আপনারা সকলেই আমার সহিত এ বিষয়ে একমত।
কিন্তু জয়দেব যে কেবলমাত্র প্রচলিত উপমাদি ব্যবহার করিয়াছেন এমন নহে, তাঁহার পরিকল্পিত দু-চারিটি নূতন উপমাও গীতগোবিন্দে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মধ্যে যেগুলি আমার নিকট বিশেষরূপে জয়দেবীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, আপনাদের জ্ঞাতার্থে তাঁহারই দুই-একটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। জয়দেব ঈশ্বরের নরহরিরূপ সম্বন্ধে বর্ণনায় বলিতেছেন—
তব করকমলবরে নখসম্ভূতশৃঙ্গম্
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
ইহার দোষ–প্রথমতঃ, কমলের নখাঘাত ও তৎকর্তৃক ভ্রমরের বিনাশ নেহাত অস্বাভাবিক; দ্বিতীয়তঃ, নরসিংহের করযুগলকে কমলের সহিত তুলনা করায় এবং হিরণ্যকশিপুকে ভৃঙ্গের সহিত তুলনা করায় উভয়ের ভিতর বৈরিতার বিরোধীভাবের পরিচয় দেওয়া হয় নাই; তৃতীয়তঃ, দুর্দান্ত দৈত্যের সহিত কৃষ্ণ নরহরিরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বধার্থ স্বীয় বীরত্বের পরিচায়ক যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাকে কমল ও ভ্রমরের যুদ্ধস্বরূপ বলায় ভাবের যাথার্থ্য এবং সৌন্দর্য কতটা পরিমাণে বজায় থাকিল আপনারাই বিবেচনা করিবেন।
বলরামকে উল্লেখ করিয়া জয়দেব বলিতেছেন—
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্
হলহতিভীতিমিলিযমুনাভম্।
হলতাড়নার ভয়ে যমুনা ডাঙায় উঠিয়া বলরামের দেহে বসনরূপে সংলগ্ন হইয়াছেন, এরূপ অযথা কথা বলায় যদি কিছু সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলেও নাহয় উপমাটি সহ্য করা যাইত; আমার বিবেচনায় জয়দেব বলরামকে জলে নামাইলে যমুনাকে আর জলছাড়া করিবার আবশ্যক হইত না কৃষ্ণের মুখ কিরূপ, না—
তরলদৃগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগ
ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগম্।
কৃষ্ণের নয়নশোভিত বদন দেখিয়া মনে হইল যেন পদ্মের ভিতর খঞ্জনযুগল খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কমলের ভিতর খঞ্জনযুগলের বিহার আমিও দেখি নাই, জয়দেবও দেখেন নাই এবং আমার বিশ্বাস ওরূপ কার্য খঞ্জনের কখনো করে না। এ উপমাটি আমার নিকট যেমন অপ্রাকৃত তেমনি অর্থশূন্য বলিয়া মনে হইতেছে।
এই আমার উপমা তিনটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য কেবল জয়দেবকে নিন্দা করা নহে; আমি এইসকল উদাহরণ হইতে জয়দেব কি জন্য এবং কি উপায়ে উপমা প্রয়োগ করিতেন তাহাই দেখাইব। এরূপ উপমা পড়িয়া আপনাদের কি মনে হয় না যে, জয়দেব কেবল উপমাপ্রয়োগ করাটা কবিতায় আবশ্যক বিবেচনায় উক্ত কার্য করিতেছেন, বাস্তবিক উপমায় কবিতার সৌন্দর্য বাড়িল কি না এবং কোনো বিশেষ ভাব পরিষ্কাররূপে তাঁহার সাহায্যে ব্যক্ত করা গেল কি না এসব কথা জয়দেবের মনেও আসে নাই। উপমা আপনা হইতেই তাঁহার কাছে আসে না, তিনি জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া আনেন অর্থাৎ তাঁহার উপমায় স্বাভাবিকতা কিছুমাত্রও নাই। তাহা কেবলমাত্র কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ। প্রমাণ, কবিরা প্রায়ই সুন্দর করযুগলকে কমলের সহিত তুলনা করেন, তাই জয়দেব নরসিংহের করযুগলকে কমলস্বরূপ বলিয়া বসিলেন এবং তাহাকে কমল বলায় হিরণ্যকশিপুকে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভৃঙ্গ বলিতে হইল। ভাবের সৌন্দর্য বজায় থাকিল কি না সে কথা ভাবিয়া আর কি করিবেন? একটি ভুলের জন্য বাধ্য হইয়া আর-একটি অন্যায় কাজ করিতে হইল। আবার দেখুন, কবির। মুখকে পদ্মের সহিত এবং নয়নযুগলকে খঞ্জনের সহিত তুলনা করেন, ইহা জয়দেবের নিকট অবিদিত ছিল না, কিন্তু নয়নশোভিত বদনকে কবিরা কি বলেন তাহা তাঁহার জানা ছিল না। কাজেই কি করেন, তিনি উপমাস্বরূপ পদ্মের সহিত মনে মনে খঞ্জনের যোগ করিয়া ফেলিলেন, অগত্যা খঞ্জনকেই কমলোদরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইল। ল্যাঠা চুকিয়া গেল, জয়দেব হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কবিতা হইল কি না সে কথা আপনারা ভাবুন।
আমি ক্রমে ক্রমে প্রমাণ করিয়াছি যে জয়দেব যখন কোনো বিষয়ের সাধারণ ভাব অথবা তাঁহার সর্বাবয়বের প্রত্যক্ষরূপ সহজভাবে কিংবা অলংকারাদির সাহায্যে উত্তমরূপ বর্ণনা করিতে অসমর্থ, তখন তাহাকে এ বিষয়েও বড় কবি বলিয়া গণ্য করা যায় না।
৫.
এখন আমি জয়দেবের ভাষা সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিয়াই আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। জয়দেবের ভাষা যে অতিশয়, সুললিত এবং শ্রুতিমধুর ইহা তো সবাদিসম্মত। এমনকি যাহার সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ তাহারাও এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। বরং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকেই উক্ত বিষয়ে জয়দেবের প্রচুর পরিমাণে প্রশংসা করিতে দেখা যায়। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, কবিতার ভাষার সৌন্দর্য হইতে ভাবের সৌন্দর্য পৃথক করা যায় না। ভাবের অনুরূপ ভাষা প্রয়োগেই যথার্থ কবিত্বশক্তির পরিচয়। যাহাদের মস্তিষ্কে ভাব ও ভাষা একত্রে গঠিত হয় না তাঁহার লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য হয় ভাব-বিষয়ে পাণ্ডিত্য নয় ভাষা-বিষয়ে ছন্দনির্মাণের কৌশল, এই দুইয়ের একটির সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। জয়দেব আমার বিবেচনায় যথার্থ উচ্চ-অঙ্গের কবিতা রচনার অক্ষমতাবশতঃ লোকসাধারণের চটক লাগাইবার অভিপ্রায়ে শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় কথার কারিগরি দেখা যায়। মনে কোনো-একটি বিশেষ ভাবের উদয় হইলে যে কথাটি স্বভাবতই মুখাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, জয়দেব সেটিকে চাপিয়া রাখেন। তাঁহার পরিবর্তে শব্দশাস্ত্র খুঁজিয়া ভাবপ্রকাশ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে অনুপযোগী আর-একটি কথা আনিয়া হাজির করেন। কালিদাসাদি যথার্থ শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাপ্রণালী স্বতন্ত্র। তাহারা স্বভাবতঃ যে কথাটি মুখে আসে সেইটি ব্যবহার করেন; তবে তাঁহাদের ভাবের সহিত আমাদের ভাবের অনেক পার্থক্য, সুতরাং যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা একান্তই দুঃসাধ্য। আপনার আমার ও জয়দেবের সহিত তাঁহাদের এইটুকুমাত্র তফাত। জয়দেবের ভাষার প্রধান দোষ সুস্পষ্ট rhythmএর অভাব। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দসকল একটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্য আর-একটির ন্যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় অকারান্ত শব্দের ব্যবহারে শব্দসকলের হ্রস্বদীর্ঘাদি প্রভেদ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায়, সুতরাং তাঁহাদের উচ্চারণের বৈচিত্র্য-অভাবে, জয়দেবের ভাষায় গাম্ভীর্যের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু বাক্যের যে অংশ কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাও গাম্ভীর্যব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে মধুর হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভাষা-সম্বন্ধেও গাম্ভীর্যযুক্ত মাধুর্য গাম্ভীর্যবিরহিত মাধুর্য অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠ এবং সম্পন্ন। গীতগোবিন্দের সহিত মেঘদূতের তুলনা করিলেই দেখা যায় গাম্ভীর্যগুণবিশিষ্ট হইয়াও শেষোক্ত কাব্যের ভাষা পূর্বোক্ত কাব্যের ভাষা হইতে কত উৎকৃষ্ট।
সমভাবে উচ্চারিত অকারান্ত শব্দের একত্রে বহুল বিন্যাসের আর-একটি দোষ আছে, তাহাতে পাঠকমাত্রেরই পক্ষে রচনার অর্থ গ্রহণ করা কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া উঠে। বিভিন্ন বিভিন্ন শব্দসকল পরস্পর হইতে বিশেষরূপে স্বতন্ত্র না হইলে পাঠকালীন তাঁহাদের প্রত্যেকের উপর নজর পড়ে না। একটি শ্লোকের অন্তর্ভুত শব্দসকলের আকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য যত সুস্পষ্ট তাঁহার অর্থও সেই পরিমাণে চট্ করিয়া বুঝা যায়। শব্দসকলের বৈচিত্র্য বজায় রাখিয়া তাঁহাদের ভিতর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া যিনি রচনাকে শ্রুতিমধুর করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ভাষার রাজা। জয়দেব তাঁহার রচনায় শব্দসকলের হ্রদীৰ্ঘাদি প্রভেদজনিত বন্ধুরতা ভাঙিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া এমন মসৃণ করিয়াছেন যে তাহা পড়িতে গেলে তাঁহার উপর দিয়া রসনা ও মন দুইই পিছলাইয়া যায়। প্রত্যেক শব্দটির উপর মন বসাইতে না পারিলে সমস্ত রচনার অর্থের উপরেও অমনোযোগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।
গীতগোবিন্দে কথার বড় একটা-কিছু অর্থ নাই বলিয়া জয়দেব যে চাতুরী করিয়া যাহাতে পাঠকের মন ভাবের দিকে আকৃষ্ট না হইতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে উক্ত প্রকার শ্লোক রচনা করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছে।
এতক্ষণ পর্যন্ত আমি শুধু জয়দেবের কবিতার দোষ দেখাইয়া আসিয়াছি। তিনি যে উৎকৃষ্ট কবিদিগের সহিত সমশ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহাই দেখানো আমার উদ্দেশ্য। যাহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিক ভাব, মানবদেহের সৌন্দর্য যাহার দৃষ্টিতে ততটা পড়ে না, যিনি মানবদেহকে কেবল ভোগের বিষয় বলিয়াই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎপরিচয় নাই, যিনি বর্ণনা করিতে হইলেই শোনা কথা আওড়ান, যাঁহার ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরী অধিক— এক কথায়, যাঁহার কাব্যে স্বাভাবিকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাকে আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি। ভরসা করি এ বিষয়ে আপনারাও আমার সহিত একমত। কিন্তু এসকল কথা সত্য হইলেও জয়দেবকে যে অনেকে বড় কবি বলিয়া মনে করেন সে কথাও তো অস্বীকার করিবার জো নাই। জয়দেব সম্বন্ধে এই সাধারণ মত কি কি কারণ -প্রসূত তাহা আমি কতকটা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি।
৬.
প্রথমতঃ, শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় জয়দেব যখন তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা প্রস্ফুটিত করিয়া তুলেন তখন তাঁহার কবিতা বিশেষরূপে স্বাভাবিক হইয়া উঠে তখন তিনি কোনোরূপ অপ্রাকৃত কিংবা অযথার্থ কথা বলেন না। যে বিষয়ে যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে তাঁহার বর্ণনায় সে অবশ্য বিলক্ষণ নিপুণ। সুরতখালসজনিত দেহের অবস্থা তিনি কত জাজ্বল্যমান করিয়া আঁকিতে পারেন। মনের ভাবের কথা নাই বলিলেন, রোমাঞ্চ শীৎকার ইত্যাদি একান্ত শারীরিক ভাব সকলের বর্ণনায় তোত তিনি কাহারও অপেক্ষা কম নন। আর তাঁহার ভাষায় গাম্ভীর্য ইত্যাদি গুণ নাই বটে কিন্তু তাহা শৃঙ্গাররসের বর্ণনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যুবতীদিগের দেহের ন্যায় তাঁহার শব্দগুলিও কুসুমসুকুমার। যখন রূপসীদিগের কবরী শিথিল হইয়া যাইতেছে, নীবিবন্ধন খসিয়া পড়িতেছে, যখন সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিতেছে তখন আর ভাষার বাঁধুনি কি করিয়া প্রত্যাশা করা যায়? রাধার দেহের ন্যায় গীতগোবিন্দের ভাষা ‘নিঃসহনিপতিতা লতা’স্বরূপ। তাই শৃঙ্গাররসবর্ণনকালে তাঁহার ভাষা ভাবের অনুরূপ। তিনি শৃঙ্গাররসের কবি। কিন্তু যে রসেরই হউন না, কবি তত বটে। এবং কবির যথার্থ রচনা যে জাতিরই হউক, লোকের ভালো লাগিবেই লাগিবে, সুতরাং জয়দেবের কাব্য সাধারণের একেবারেই অনাদরের সামগ্রী নহে।
দ্বিতীয়তঃ, সাধারণের সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতা আর-একটি কারণ। সংস্কৃত না জানার দরুন ভাষার লালিত্য হইতে লোকে ধরিয়া নেয় ভাবেরও অবশ্য সৌন্দর্য আছেই আছে।
তৃতীয়তঃ, রাধাকৃষ্ণের প্রেম জয়দেবের কাব্যের বিষয় বলিয়া সাধারণের নিকট জয়দেবের কাব্য এত উপাদেয়। এ সংসারে ফুল জ্যোৎস্না মলয়পবন কোকিলের কুহুস্বর আমাদের সকলেরই ভালো লাগে, চিরদিন লোকের ভালো লাগিয়াছে এবং চিরদিন ভালো লাগিবে। কিন্তু কতকগুলি জিনিস আছে যাহার যথার্থ একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য না থাকিলেও অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ আমাদের ভালো লাগে। যমুনার জল, তমালের বন, বৃন্দাবন, মথুরা, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি— এসকলের মধুরতা পূর্ণিমারজনী দক্ষিণপবনের ন্যায় আমাদের নিকট পুরাতন হয় না। যিনিই এসকলের কথা বলেন, তাঁহার কথাই আমাদের শুনিতে ইচ্ছা যায়। আমরা অনেকেই বৃন্দাবন, যমুনার জল এসকল কিছুই দেখি, নাই, বাঁশির সুরও কখনো শুনি নাই তবে তাঁহাদের কথা এত প্রাণ স্পর্শ করে কেন? কারণ ঐ এক-একটি কথা হৃদয়ে কত সুন্দর কত মধুর স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। আমরা যমুনার জল দেখি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এত সুন্দর কবিতা পড়িয়াছি যে, যমুনার সমস্ত সৌন্দর্য আমাদের হৃদয়ে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়সম্পৰ্কীয় সকল বস্তুকেই প্রকৃতির চিরস্থায়ী সুন্দর অংশসকলের মধ্যে ভুক্ত করিয়া ফেলি। সুতরাং জয়দেব যখন সেই যমুনা, সেই বাঁশি, সেই রাধা, সেই কৃষ্ণ ও সেই বৃন্দাবনের কথা বলেন তখন তাঁহার পরিবর্তে তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবিরা আমাদের মনে ঐসকলের যে সুন্দর মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহারই দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। আমরা আসল কারণ না বিচার করিয়া মনে করি জয়দেবের কবিতা পড়িয়াই আমরা মোহিত হইতেছি। তাঁহার পরবর্তী কবিসকলের গুণ আমরা ভুলক্রমে জয়দেবে আরোপ করি। চণ্ডীদাসাদি বৈষ্ণবকবিগুণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাব্যের বিষয় না করিলে জয়দেব আমাদের যতটা ভালো লাগে তাহা অপেক্ষা অনেক কম ভালো লাগিত, অন্ততঃ আমার কাছে।
১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ
———-
(১) যেকালে এ প্রবন্ধ লেখা হয়, সেকালে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের কোনো গ্রন্থ আমি চোখে দেখি নি, এমনকি তাদের নাম পর্যন্ত শুনি নি, সেই কারণে উক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যটি আমি আমাদের দেশে প্রচলিত বাক্য বলে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছিলুম। -লেখক। ১৩২৭
পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ
আমার বিশ্বাস, নবাবি আমলের বঙ্গসাহিত্যের অন্তর থেকে অনেক ছোটখাট ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করা যায়। বলা বাহুল্য, সত্য মাত্রেই ঐতিহাসিক সত্য নয়, যেমন fact মাত্রেই scientific fact নয়। সত্যেরও একটা জাতিভেদ আছে।
ইতিহাসেরও একটা Evidence Act আছে। যে ঘটনা উক্ত আইনের বাঁধাধরা নিয়মের ভিতর ধরা না পড়ে, সে ঘটনা যে সত্য, এ কথা ইতিহাসের আদালতে গ্রাহ্য হয় না। সুতরাং যে-ঘটনা আমরা মনে জানি সত্য, তা যে ঐতিহাসিক সত্য, এমন কথা মুখ ফুটে বলবার সাহস পাই নে, রীতিমত দলিলদস্তাবেজের অভাবে।
আর বাংলা সাহিত্যে যে শুধু ছোটখাট ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তার কারণ সেকালে কোনো বাঙালি ইতিহাস লেখেন নি, লিখতে চেষ্টাও করেন নি; প্রসঙ্গতঃ এখানে-ওখানে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যার গায়ে সত্যের স্পষ্ট ছাপ আছে। আর আমার বিশ্বাস যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে ছোট-বড়র বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। সত্যের যদি কোনো মূল্য থাকে তো সে মূল্য ছোটর অন্তরেও আছে, বড়র অন্তরেও আছে। সুতরাং সেকেলে বঙ্গসাহিত্যের অন্তরে যেসকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলি তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করবার জিনিস নয়।
চৈতন্যচরিতামৃতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যে অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে ঘটনা যে প্রকৃত, কবিকল্পিত নয়, এই আমার চিরকেলে ধারণা। এবং এর ফলে, যাঁরা ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন, উক্ত ঘটনাটির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। পূর্বে যে করি নি, সে কতকটা আলস্য ও কতকটা সংকোচবশতঃ। সম্প্রতি শ্ৰীযুক্ত অমৃতলাল শীল উক্ত ঘটনা অবলম্বন করে প্রবাসী পত্রিকায় একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন।
তিনি বলেন যে, তারও বিশ্বাস ও-গল্পটি বৈষ্ণবদের কল্পিত নয়, সত্য ঘটনা। আমরা যদি সে যুগের ইতিহাসের অন্তর থেকে পাঠান-বৈষ্ণব বিজুলি খাকে বার করতে পারি, তাহলে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত বিবরণ যে সত্য সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। উক্ত কারণেই শীল মহাশয় বিজুলি খাঁর পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, চৈতন্যচরিতামৃতে যাকে বিজুলি খাঁ বল। হয়েছে, তার প্রকৃত নাম আহম্মদ খা। আমার ধারণা অন্যরূপ। আমার। বিশ্বাস, চৈতন্যের যুগে বিজুলি খাঁ নামে একটি স্বতন্ত্র ও স্বনামখ্যাত রাজকুমার ছিলেন, এবং কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তারই কথা বলেছেন। কি কারণে আমার মনে এ ধারণা জন্মেছে, সেই কথাটাই এ প্রবন্ধে বলতে চাই।
২.
চৈতন্যচরিতামৃত হতে যদি সমগ্র বর্ণনাটি পাঠকদের চোখের সুমুখে ধরে দিতে পারতুম, তাহলে ঘটনাটি যে কত অদ্ভুত তা সকলেই দেখতে পেতেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের ভিতর তার অবসর নেই, কারণ বর্ণনাটি একটু লম্বা। তা ছাড়া যিনি ইচ্ছা করেন, তিনিই চৈতন্যচরিতামৃতে তা দেখে নিতে পারেন। আমি সংক্ষেপে এবং যতদূর সম্ভব কবিরাজ মহাশয়ের জবানিতেই ব্যাপার কি হয়েছিল বলবার চেষ্টা করব। কারণ ঘটনাটি না জানলে তার বিচার পাঠকদের মনে লাগবে না। ঘটনাটি অদ্ভুত হলেও যে মিথ্যা নয়, এবং একেবারে বিচারসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য, তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। সকলেই মনে রাখবেন যে, ঐতিহাসিক সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। অতীতে যা একবার ঘটেছিল, তা পৃথিবীতে আর দু’বার ঘটে না। ইংরেজিতে যাকে বলে historical fact, তার repetition নেই। আর যে-জাতীয় ঘটনা বার-বার ঘটে এবং ঘটতে বাধ্য, সেই জাতীয় ঘটনা নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার। সুতরাং ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমরা যাকে প্রমাণ বলি, তা অনুমান মাত্র।
মহাপ্রভু বৃন্দাবন-অঞ্চলে তীর্থভ্রমণ করে দেশে যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন একদিন পথশ্রান্তি দূর করবার জন্য একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় নেন। তার সঙ্গী ছিল তিনটি বাঙালি শিষ্য আর দুটি হিন্দুস্থানি ভক্ত; একজন রাজপুত অপরটি মাথুর ব্রাহ্মণ। এ দুই ব্যক্তিকেই তিনি মথুরাতে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি গাছতলায় বসে আছেন, এমন সময়–
আচম্বিতে এক গোপ বংশ বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল।।
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িল।
মুখে ফেন পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈল।।
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
স্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা।।
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার।।
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লইয়া।।
যবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া কাঁপিতে লাগিল।।
এর থেকে বোঝা যায় যে, ভয় জিনিসটে আমরা বিলেত থেকে আমদানি করি নি। বাঙালি তিনজন ভয়ে কাপতে লাগলেন দেখে মহাপ্রভুর হিন্দুস্থানি ভক্ত দু জন তাঁদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। কারণ—
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়।।
সেই ‘মুখে বড় দড়’ ব্রাহ্মণ পাঠান আসোয়ারদের বললেন–
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েত মূর্ছিত।
অবহি চেতনা পাব হইব সংবিত।।
ক্ষণেক ইহা বৈস বান্ধি রাখহ সবারে।
ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে।।
এ কথা শুনে
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা দুইজন।
গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে তিনজন।।
বাঙালি বেচারারা ভয়ে কাঁপছে, তার থেকে প্রমাণ হল তারাই মহাপ্রভুকে খুন করেছে। একালেও আদালতে demeanour থেকে অপরাধের প্রমাণ হয়। সুতরাং সে তিন বেচারার হাতে হাতে প্রাণদণ্ড দেওয়াই স্থির হল। এ ক্ষেত্রেও উক্ত গোবেচারাদের প্রাণরক্ষা করলেন সেই নির্ভীক রাজপুত বৈষ্ণব।
কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
দুইশত তুরুকী আছে দুই শত কামানে।।
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সব মারি।।
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার।।
শুনিয়া পাঠানমনে সংকোচ বড় হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল।।
এর পর পাঠানদের মধ্যে যে একজন পীর ছিলেন, তার সঙ্গে মহাপ্রভুর শাস্ত্ৰবিচার শুরু হয়, এবং সে বিচারে পরাস্ত হয়ে পীর সাহেব মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং–
রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলিখান।।
অল্পবয়স তার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার।।
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেহ মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাঁহার মাথায়।।
এই হচ্ছে পূর্বোক্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
পীর ও প্রভুর শাস্ত্ৰবিচারের পরিচয় পরে দেব; কারণ সে বিচার অতি বিস্ময়জনক। তার পর কি কারণে রাজকুমার বিজুলি খাঁকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করি তা বলব। প্রথমে এ রকম ঘটনা ঘটা যে সম্ভব তাই দেখাবার জন্য দেশ-কালের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।
৩.
শীল মহাশয় অনুমান করেন যে, মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন-অঞ্চলে তীর্থভ্রমণে যান তখন সিকন্দর লোদি দিল্লীর পাতশা, এবং আগ্রা ছিল তার রাজধানী। ১৫১৭ খৃস্টাব্দে সিকন্দর লোদীর মৃত্যু হয়। সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লিখিত ঘটনা সম্ভবতঃ ১৫১৬ খৃস্টাব্দে ঘটে। আমার বিশ্বাস, এ অনুমান সংগত। কবিরাজ গোস্বামীর কথা মেনে নিলেও ঐ তারিখই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে মহাপ্রভুর–
মধ্যলীলার করিল এই দিগদরশন।
ছয় বৎসর করিল যৈছে গমনাগমন।।
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্তন-উল্লাস॥ (চৈতন্যচরিতামৃত, ২৫ পরিচ্ছেদ, ১৮৫ শ্লোক।)
এখন, ঐতিহাসিকদের মতে চৈতন্যদেব চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং তার কিছুদিন পরেই তীর্থপর্যটনে বহির্গত হন। ঠিক কতদিন পরে তা আমরা জানি নে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে তাঁর ‘গমনাগমন’ শুরু হয় ১৫১০ খৃস্টাব্দে, তাহলে তিনি কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের হিসেবমত ১৫১৬ সালে ‘মথুরা হইতে প্রয়াগ’ গমন করেন। অপর পক্ষে তার মৃত্যুর আঠারো বৎসরের আগের হিসেব ধরলেও ঐ একই তারিখে পৌঁছনো যায়, কারণ মহাপ্রভুর তিরোভাবের তারিখ হচ্ছে ১৫৩৪ খৃস্টাব্দ।
সিকন্দর লোদি ছিলেন হিন্দুধর্মের মারাত্মক শত্রু। উক্ত পাতশার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কথা-ক’টি হতে পাওয়া যাবে–
The greatest blot on his character as relentless bigotry. The Wholesale destruction of temples was not the best method of conciliating the Hindus of a conquered district. (Cambridge History of India, Vol. 3, p. 246.)
চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, তখন সে দেশে যে দেবমন্দির ও বিগ্রহাদির ধ্বংসলীলা চলছিল, তা চৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নেদ্ধৃত শ্লোকগুলি হতেই জানা যায়। মহাপ্রভু অতিকষ্টে গোপালজির দর্শনলাভ করেন। কারণ–
অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি।।
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল।।
আজি রাত্রে পলাহ না রহিও এক জন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালযবন।।
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠুলি গ্রামে থুইল।।
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সবজন।।
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে।।
পূর্বোক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক সিকন্দর লোদি সম্বন্ধে আরও বলেন যে–
The accounts of his conquests resemble those of the protagonists of Islam in India. Sikandar Lodi’s mind was warped by habitual association with theologians.
পাঠান বীরপুরুষের প্রথম যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তারা যেভাবে হিন্দু মন্দির-মঠ-দেবদেবীর উপর যুদ্ধঘোষণা করেন, তার পাঁচ শ বৎসর পরে পাঠানরাজ্যের যখন ভগ্নদশা, তখন আবার পাঠান পাতশারা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নব জেহাদ প্রচার করেন কেন? যেকালে সিকন্দর লোদি বৃন্দাবন-অঞ্চলে দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করেন, ঠিক সেই একই সময়ে গৌড়ের পাতশা হুসেন শাহও–
ওড্রদেশে কোটিকোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক, কতকত করিল প্রমাদ।। (চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়)
৪.
এই সময়েই হিন্দুধর্ম নূতন প্রাণ পায়। তাই উক্ত ধর্মের প্রতি পাতশাদের মনে নববিদ্বেষও জাগ্রত হয়। এই নবহিন্দুধর্ম নবরূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়। জ্ঞান-কর্মকে প্রত্যাখ্যান করে এ ধর্ম একমাত্র ভক্তিপ্রধান হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানন্দ যে ভক্তির ধর্ম উত্তরাপথে প্রচার করেন, সে ধর্ম বহুলোকের হৃদয়-মন স্পর্শ করে। ‘শুষ্ক জ্ঞান’ ও ‘বাহ্যকর্মের’ ব্যবসায়ীদের, অর্থাৎ হিন্দুসমাজের ধর্মযাজকদের ও বেদান্তশাস্ত্রীদের, যে এই ভক্তিধর্মের প্রতি অসীম অবজ্ঞা ছিল, তার প্রমাণ বৈষ্ণবগ্রন্থে পাতায় পাতায় আছে।
অপর পক্ষে মৌলবিদের অর্থাৎ মুসলমান ধর্মশাস্ত্রীদের বিদ্বেষের একটি বিশেষ কারণ ছিল। তারা ভয় পেয়েছিলেন যে, এই প্রবল ভক্তির স্রোতে অনেক মুসলমানও হয়তো ভেসে যাবে, এবং আমার বিশ্বাস, এই শাস্ত্রীদের দ্বারা প্রচোরিত হয়েই সেকালের মুসলমান পাতশারা এই নবহিন্দুধর্মের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেন। অন্ততঃ সিকন্দর লোদির মন তো was warped by habitual association with theologians.
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল সেকালের জনৈক ব্রাহ্মণের নবধর্মমত প্রচার করার অপরাধে প্রাণদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। Cambridge History of India থেকে উক্ত ঘটনাটির বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—
Sikandar had an opportunity while at Sambul of displaying the bigotry which was a prominent feature of his character. A Brahman of Bengal excited some interest and, among precisians, much indignation, by publicly maintaining that the Mahomedan and Hindu religions were both true, and were but different paths by which God might be approached. Azam-i-Humayun, governor of Bihar, was directed to send the daring preacher and two rival doctors of Islamic law to court, and theologians were summoned from various parts of the kingdom to consider whether it was permissible to preach peace. They decided that since the Brahman had admitted the truth of Islam, he should be invited to embrace it with the alternative of death in the event of refusal. The decision commended itself to Sikandar and the penalty was exacted from the Brahman, who refused to change his faith.
এ বাঙালি ব্রাহ্মণটি যে কে জানি নে। কিন্তু তার সমকালবর্তী কবীরের মতও ঐ, চৈতন্যেরও তাই। চৈতন্যের শিষ্য যবন হরিদাসের যখন গৌড়ের বাদশার দরবারে বিচার হয়, তখন হরিদাসও ঐ একই মত প্রকাশ করেন, এবং বাংলার ও আগ্রার মৌলবিদের মতে যে it was not permissible to preach peace, তার কারণ তারা ভয় পেয়েছিলেন যে উক্ত ধর্মের প্রশ্রয় দিলে কোনো কোনো পাঠানও এই নববৈষ্ণবতন্ত্রে দীক্ষিত হবে, যেমন বিজুলি খাঁ। পরে হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, আদিতে এই বৈষ্ণবধর্ম একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম ছিল না। পূর্বোক্ত বাঙালি ব্রাহ্মণ যেমন স্বধর্ম ত্যাগ না করেও মুসলমান ধর্মের অনুকূল হয়েছিলেন, আমার বিশ্বাস কোনো কোনো পাঠানও তেমনি স্বধর্ম ত্যাগ না করেও পরমভাগবত হয়েছিলেন, এবং বিজুলি খাঁ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।
৫.
এখন প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক। যে অবস্থায় ও যে কারণে মহাপ্রভুর দলবল পথ-চলতি তুরুখ-সোয়ারদের হাতে গ্রেপ্তার হন, তার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ঐ সূত্রে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলেছেন যে—
সেই ম্লেচ্ছমধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল বস্ত্র পরে তা’তে লোকে কহে পীর।
এই পীবের সঙ্গে মহাপ্রভু শাস্ত্ৰবিচার করে তাকে স্বমতাবলম্বী করেন। পরে পাঠান রাজকুমার বিজুলি খাঁও স্বীয় গুরুর পদানুসরণ করেন। এই শাস্ত্ৰবিচারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব, কারণ এ বিচার অদ্ভুত। সেই পীরের–
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুরে দেখিয়া
এবং সে
নির্বিশেষ ব্ৰহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্ৰ উঠাইয়া।।
অদ্বয় ব্ৰহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিলা খণ্ডন।।
মুসলমান পীর যে শংকরপন্থী অদ্বৈতবাদী, এ কথা কি বিশ্বাস্য? তার পর মহাপ্রভুর উত্তর আরও আশ্চর্য। তিনি বললেন–
তোমার পণ্ডিত সবের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব পর বিধিমধ্যে পর বলবান্।।
নিজ শাস্ত্র দেখি তুমি বিচার করিয়া।
কি লিখিয়াছে শেষ নির্ণয় করিয়া।
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে স্থপ নির্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ।।
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ তেহে শ্যামকলেবর।।
সচ্চিদানন্দ দেহ পূর্ণব্রহ্মরূপ।
সর্বাত্মা সর্বজ্ঞ নিত্য সর্বাদিম্বরূপ।
মহাপ্রভুর মুখে এ কথা শুনে পীর উত্তর করলেন যে–
অনেক দেখি মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধনবস্তু নারি নির্ধারিতে।।…
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান।।
এই কথোপকথন আমাদের বড়ই আশ্চর্য ঠেকে, কারণ মুসলমান ধর্মের God যে personal God, বহু দেবতাও নয়, এক নির্গুণ পরব্রহ্মও নয়, এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং কোনো পরমগম্ভীর মুসলমান পীরকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে মহাপ্রভুর পক্ষে আবশ্যক হয়েছিল, এ কথাটা প্রথমে নিতান্তই আজগুবি মনে হয়। কিন্তু যাদের মুসলমান ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তারা জানেন যে, কালক্রমে মুসলমান ধর্মও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে, এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রদায় জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে, এবং কোনো ধর্মেরই জ্ঞানমার্গীরা সগুণ ঈশ্বর অঙ্গীকার করে না। উক্ত পীর যে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তা তাঁর পরিধানের কালো বস্তু থেকেই বোঝা যায়। সুফীদের সাম্প্রদায়িক বেশ স্বতন্ত্র। সুতরাং পীর মহাশয় সুফী নন। তবে তিনি কি? যারা মুসলমান ধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলতে পারেন।
তার পর আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মহাপ্রভুর মুসলমান শাস্ত্রের বিচার। শ্রীচৈতন্য যে মহাপণ্ডিত ছিলেন তা আমরা সকলেই জানি, তবে তিনি যে আরবি শাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন, এ কথা কারও মুখে শুনি নি। তবে এ বিচারের কথাটা কি আগাগোড়া মিথ্যা? আমার ধারণা অন্যরূপ। আমার বিশ্বাস, সে-যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতমহলে শাস্ত্ৰবিচার চলত, এবং হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্রীরা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মমতের আসল কথা সব জানতেন। সিকন্দর লোদি গোঁড়া মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার দরবারে জনৈক বাঙালি ব্রাহ্মণের সহিত মৌলবিদের শাস্ত্ৰবিচারের বৈঠক বসান। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয় তো মহাপ্রভু যে মুসলমান শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হন, এ কথা অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই।
৬.
কবিরাজ গোস্বামীর এসব কথা যদি সত্য হয়, এবং আমার বিশ্বাস তা মূলতঃ সত্য, তাহলে এই প্রমাণ হয় যে, মহাপ্রভু যেমন পুরীতে সার্বভৌমকে, কাশীতে প্রকাশানন্দকে, জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করতে বাধ্য। করেছিলেন, তেমনি তিনি সৌরক্ষেত্রে জনৈক পরমগম্ভীর অদ্বৈতবাদী মুসলমান পীরকেও ভগবদ্ভক্ত করে তুলেছিলেন, এবং একমাত্র কোরানের দোহাই দিয়ে। এবং তিনি পূর্বেও যেমন হিন্দু শাস্ত্রীদের নিকট মুসলমান ধর্ম প্রচার করেন নি, এ ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি মুসলমান শাস্ত্রীর নিকট হিন্দুধর্ম প্রচার করেন নি। কিন্তু উভয় ধর্মমতেরই যা greatest common ineasure, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি, তারই মর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং আমার বিশ্বাস, ইতিপূর্বে সিকন্দর লোদি যে-ব্রাহ্মণ বেচারাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, সে বেচারির অপরাধ সে একই মত প্রচার করে, কিন্তু তাই বলে স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম অঙ্গীকার করতে রাজি হয় না–প্রাণ বাঁচাবার খাতিরেও নয়।
ও-যুগটা ছিল এ দেশের ধর্মের ইন্টারন্যাশনালিজমের যুগ। আজও এমন বহু লোক আছেন যারা ইন্টারন্যাশনালিজম কথাটায় ভয় পান, কারণ তাদের বিশাস ও-মনোভাব ন্যাশনালিজমের পরিপন্থী। সেকালেও অনেকে ধর্ম বলতে বুঝতেন, হয় হিন্দুধর্ম, নয় মুসলমান ধর্ম। কিন্তু মানুষে যাকে ধর্মমনোভাব বলে, তার প্রাণ যে ভগবদ্ভক্তি, এ জ্ঞান যার আছে, তার অন্তরে নানা ধর্মের ভেদজ্ঞানটাই অবিদ্যা। আমার বিশ্বাস, সে যুগে ভগবদ্ভক্ত ও বৈষ্ণব এ দুটি পর্যায়-শব্দ ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণের মত পাঠানও স্বধর্ম রক্ষা করেও পরমবৈষ্ণব অর্থাৎ পরমভাগবত হতে পারত। সকল ধর্মেরই কথা এক, শুধু ভাষা বিভিন্ন। বৈষ্ণবধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে–
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
এ কথা বলাও যা আর স্বধর্ম রক্ষা করে মামেকং শরণং ব্রজ, এ কথা বলাও কি তাই নয়?
৭.
হিন্দু যে স্বধর্ম ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, এ ঘটনা আজও ঘটে, কিন্তু মুসলমান যে স্বধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, আজ তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণেই চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, হিন্দুধর্ম অর্থাৎ হিন্দুসমাজের দরজা আজ বন্ধ হলেও অতীতে খোলা ছিল। আজ আমরা এ সমাজ থেকে অনেক হিন্দুকে বহিষ্কৃত করতে পারি, কিন্তু কোনো অহিন্দুকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি নে, কারণ আজকের দিনে হিন্দুসমাজের অর্থ হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্মের অর্থ হিন্দুসমাজ। আর হিন্দুসমাজ হচ্ছে অপর সকল মানবসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন ও একঘরে; কিন্তু ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন যে, হিন্দুযুগে অসংখ্য শক ও যবন বৌদ্ধধর্মের শরণ গ্রহণ করেন, এবং বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা মাত্র; আর এ ধর্মমন্দিরের দ্বার বিশ্বমানবের জন্য উন্মুক্ত ছিল।
ভারতবর্ষের মধ্যযুগের এই নববৈষ্ণবধর্মও সনাতন হিন্দুধর্মের একটি নব শাখা মাত্র। তবে ও নবত্বের কারণ, মুসলমান ধর্মের প্রভাব। মুসলমান ধর্ম যে প্রধানতঃ ঐকান্তিক ভক্তির ধর্ম, এ কথা কে না জানে? ভারতবর্ষের মধ্যযুগের বৈষ্ণবধর্ম যে মুসলমান ধর্মের এতটা হিন্দুধর্ম ও মুসলমান ধর্ম পাশাপাশি বাস করে আসছিল। একেশ্বরবাদ, ও মানুষমাত্রেই যে ভগবানের সন্তান, এ দুটিই হচ্ছে মুসলমান ধর্মের বড় কথা। তাই এই নবহিন্দুধর্মে অহিন্দুরও প্রবেশের পূর্ণ অধিকার ছিল। তা যে ছিল, তার প্রমাণ চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে দেদার আছে। সুতরাং শীল মহাশয়ের আবিষ্কৃত মহম্মদ খাঁ নামক পাঠানও যে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত হন, এ কথা অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। তবে বিজুলি খাঁ নামক যে একটি স্বতন্ত্র পাঠান রাজকুমার ছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই, এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁর সঙ্গে চৈতন্যদেবের মথুরার সন্নিকটে দেখা হয়েছিল। Tabakat-i-Akbari নামক ফারসি গ্রন্থে তাঁর নামধাম এবং তার বাপের নামও পাওয়া যায়। আকবর কর্তৃক কালিঞ্জর-দুর্গ আক্রমণসূত্রে গ্রন্থকার বলেন যে—
This is a strong fortress, and many former Sultans had been anibitious of taking it. Sher Khan Afghan (Sher Shah) besieged it for a year, but was killed in the attempt to take it, as has been narrated in the history of his reign. During the interregnum of the Afghans, Raja Rain Chunder liad purchased the fort at a high price from Bijilli Kian, the adopted son (Pisan-i-khvanda) of Bihar Khan Afghan. (Elliots’ History of India, Vol. I, p. 333)
এর থেকে জানা যায় যে, রাজকুমার বিজুলি খাঁ কালিঞ্জরের নবাবের পোষ্যপুত্র; এবং তিনিই এ রাজ্য রাজা রামচন্দ্রকে বিক্রি করে চলে গিয়েছিলেন, সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে। তবে তিনি যে কবে কালিঞ্জর-রাজ্য ত্যাগ করেন তার তারিখ আমরা জানি নে, সম্ভবতঃ তার পিতা বিহারি খা অফিগানের মৃত্যুর পর তিনি যখন স্বয়ং নবাবু হন। শের শাহর মৃত্যু হয়েছিল ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে, বিজুলি খাঁ খুব সম্ভবত এর পরেই কালিঞ্জর হস্তান্তর করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর অল্প বয়েস, সুতরাং রাজা রামচন্দ্রকে তিনি যখন কালিঞ্জর-দুর্গ বিক্রি করেন, তখন তার বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। বিজুলি খাঁ কালিঞ্জরের নবাবু হওয়া সত্ত্বেও যে পরমভাগবত বলে গণ্য হয়েছিলেন, এ ব্যাপার অসম্ভব নয়। বৌদ্ধযুগের বড় বড় রাজামহারাজারাও পরমসৌগত বলে গণ্য হতেন। তা ছাড়া, এ নববৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করবার প্রয়োজন ছিল না। ভোগে অনাসক্ত হলেই বৈষ্ণব হওয়া যেত। মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে এই কথা বলেই তাকে সংসারত্যাগের সংকল্প হতে বিরত করেন।
মহাপ্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অপরকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে কখনও উৎসাহ দেন নি। এমনকি, বালযোগী অবধূত নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর ধর্ম ত্যাগ করে গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিলেন।
এইসব কারণে আমার বিশ্বাস যে, চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত উক্ত ঘটনাটি অন্ততঃ চৌদ্দ আনা সত্য, অতএব ঐতিহাসিক। কারণ আমরা যাকে ঐতিহাসিক সত্য বলি, তার ভিতর থেকে অনেকখানি খাদ বাদ না দিলে তা বৈজ্ঞানিক সত্য হয় না। ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে অসত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মাঝামাঝি একরকম সত্যাসত্য মাত্র। আর-এক কথা। আমরা যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনেক কথাই কবিকল্পিত মনে করি, তার কারণ সেকালের অনেক পুঁথি কাব্য হিসেবে পড়ি, যদিচ কাব্যের কোনো লক্ষণই তাদের গায়ে নেই, এক পয়ারের বন্ধন ছাড়া। পরে সে পয়ারের বন্ধন যে কত ঢিলে আর তার শ্রী যে কত চমৎকার, তা চৈতন্যচরিতামৃতের উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে সকলেই দেখতে পাবেন। তা ছাড়া ওসব গ্রন্থে কবিকল্পিত, অর্থাৎ কবির কল্পনাপ্রসূত বলে কোনো জিনিসই নেই। কবিকল্পনার তাঁরা ধার ধারতেন না। সুতরাং তাদের কথার যদি কোনো মূল্য থাকে, তা একমাত্র সত্য হিসাবে।
সুতরাং লিটারেচার ওরফে রস-সাহিত্য যাদের মুখরোচক নয় এবং যারা মাত্র সত্যানুসন্ধী, তাঁদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নির্ভয়ে চর্চা করতে অনুরোধ করি। তারা ও সাহিত্যের অন্তরে অনেক নীরস ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান নিশ্চয় পাবেন।
১৩৩৮ বৈশাখ
ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়
রামমোহন লাইব্রেরিতে পঠিত
আমি আপনাদের সুমুখে ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে প্রস্তুত হয়েছি, এ সংবাদ শুনে আমার কোনো শুভার্থী বন্ধু অতিশয় ব্যতিব্যস্তভাবে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, ‘তুমি ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে এত কম জানো যে, আমি ভেবে পাচ্ছি নে কি ভরসায় তুমি এ কাজ করতে উদ্যত হয়েছ।‘ আমি উত্তর করি, এই ভরসায় যে, আমার শ্রোতৃমণ্ডলী এ বিষয়ে আমার চাইতেও কম জানেন।
এ কথা স্বীকার করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি যৎসামান্য; কেননা সে সাহিত্য এত বিপুল ও এত বিস্তৃত যে, তার সম্যক্ পরিচয় লাভ করতে একটি পুরো জীবন কেটে যায়। খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দী হতে আরম্ভ করে অদ্যাবধি এই ন’ শ বৎসর ধরে ফরাসি জাতি অবিরাম সাহিত্যসৃষ্টি করে আসছে। সুতরাং ফরাসি সরস্বতীর ভাণ্ডারে যে ঐশ্বর্য সঞ্চিত রয়েছে তার আদ্যোপান্ত পরিচয় নেবার সুযোগ এবং অবসর আমার জীবনে ঘটে নি। এর যে অংশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে, সে হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যসাহিত্য। প্রাচীন ফরাসি সাহিত্যের উদ্যানে আমি শুধু পল্লব গ্রহণ করেছি। কিন্তু এই স্বল্পপরিচয়ের ফলে আমার মনে ফরাসি সভ্যতার প্রতি একটি আন্তরিক অনুরাগ জন্মলাভ করেছে। সে সাহিত্যের এমন-একটি মোহিনীশক্তি আছে যে, যিনিই তার চর্চা করেন তারই মন ফরাসি সভ্যতার প্রতি একান্ত অনুকূল হয়। যিনিই ফরাসি সাহিত্য ভালোবাসেন তিনিই ফরাসি জাতির সুখের সুখী ব্যথার ব্যথী হয়ে ওঠেন। আজকের দিনে ফ্রান্স তার জাতীয় জীবনের অণুপরমাণুতে যে অত্যাচারের বেদনা অনুভব করছে আমরাও তার অংশীদার। জর্মানির দেহবলের নিকট ফ্রান্সের আত্মবল, জার্মানির যন্ত্রশক্তির নিকট ফ্রান্সের মন্ত্রশক্তি যদি পরাভূত হয়, যদি এই যুদ্ধে ফরাসি সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ইউরোপের মনোজগতের আলল নিবে যাবে। কি গুণে ফ্রান্স অপর জাতির ভক্তি ও প্রতি আকর্ষণ করতে পারে সে বিষয়ে সুবিখ্যাত মার্কিন নভেলিস্ট হেনরি জেমসের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি–
Our heroic friend sums up for us, in other words, and has always summed up), the life of the mind and thc life of the senses alike, taken together, in the most irrepressible freedom of eitlier, and, after that fashioil, 190sitively lives for us, carries on experience for us…
She is sole and single in this, that she takes charge of those of the interests of man which most dispose him to fraternise with himself, to pervade all his possibilities and to taste all his faculties, and in consequency to find and to make the earth a friendlier, an casier, and specially a more various syjourn…
She has gardened where the soil of humanity lias been most grateful and the aspect, so to call it, most toward the suin, and there at the high and yet mild and fortunate centre, she has grown the precious, intimate, the nourishing, finishing things that she has inexhaustively scattered alsroad. (The Book of Face, Macmilal & Co., 1915.) এই কথাগুলি যেমন সুন্দর তেমনি সত্য।
ইহজীবনে আমাদের দেহমনের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় পরস্পর-অনুপ্রবিষ্ট। এই সত্যের উপরই ফরাসি সাহিত্যের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। ফরাসি জাতি চিন্তারাজ্যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে মিথ্যা বলে উড়িয়েও দেয় নি, অকিঞ্চিৎকর বলেও উপেক্ষা করে নি; সুতরাং ফরাসি সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স এবং আর্টের একত্রে সাক্ষালাভ করা যায়। হেনরি জেম্স বলেছেন যে, ফরাসি জাতি বিশেষ করে সেইসকল মনোভাবের অনুশীলন করেছেন যাতে করে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা জন্মায়। এই গুণেই ফরাসি সভ্যতা পরকে আপন করতে পারে। ফরাসি সাহিত্য প্রধানতঃ মানবমনের সাধারণ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই তা সর্বলোকগ্রাহ্য এবং সর্বলোকপ্রিয়। বসুধৈব কুটুম্বক ফরাসি সভ্যতার এই বীজমন্ত্র কোনো ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আপনারা সকলেই জানেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর যে সকল ফরাসি দার্শনিক বিশ্বমৈত্রীর বার্তা ঘোষণা করেন, তারা প্রায় সকলেই নাস্তিক ছিলেন। মানবচরিত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরেই ফরাসি মনোভাব প্রতিষ্ঠিত, এবং সে মনোভাব প্রধানতঃ ফরাসি সাহিত্যই গঠিত করে তুলেছে। হেনরি জেমস বলেছেন যে, ফরাসি মনের চোখ চিরদিনই আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। দিনের আলোয় যা দেখা যায় না, ফরাসি মন স্বভাবতই তা দেখতে চায় না। এর ফলে যে মনোভাব অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যে সত্য ধরা দেয় না, শুধু আভাসে ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় দেয়, সে মনোভাবের, সে সত্যের সাক্ষাৎ ফরাসি সাহিত্যে বড়-একটা পাওয়া যায় না। সরস্বতীদর্শনের কাল, ফরাসি কবিদের মতে গোধূলিলগ্ন নয়। যা কেবলমাত্র কল্পনার ধন, সে ধনে ফরাসি সাহিত্য অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। অপর পক্ষে এই আলোকপ্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপূর্ব স্বচ্ছতা, অপূর্ব উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। এর তুল্য স্পষ্টভাষী সাহিত্য ইউরোপে আর দ্বিতীয় নেই। আমরা টস্পষ্টভাষী’ শব্দ সচরাচর যে অর্থে ব্যবহার করি, সে অর্থে এ সাহিত্য স্পষ্টভাষী নয়। যিনি দিবারাত্র অপরকে অপ্রিয় কথা বলতে ব্যস্ত, এ দেশে আমরা তাকেই স্পষ্টবক্তা বলি— ভাষায় যাকে বলে ঠোঁটকাটা। ফরাসি সাহিত্য কিন্তু ঠোঁটকাটা সাহিত্য নয়। ফরাসি জাতির ক্ষাত্রধর্ম জগৎ-বিখ্যাত। ফরাসি লেখকেরা বাক্যুদ্ধেও সভ্যতার আইনকানুন মেনে চলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁরা ধর্মযুদ্ধের পক্ষপাতী। ফরাসি জাতি হাসতে জানে, তাই তারা কথায় কথায় ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠে না। তীক্ষ্ণ হাসির যে কি মর্মভেদী শক্তি আছে, এ সন্ধান যারা জানে তাদের পক্ষে কটুকাটব্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক। যার হাতে তরবারি আছে, সে লগুড় ব্যবহার করে না। ভল্টেয়ারের হাসির যে বিশ্বজয়ী শক্তি ছিল, তার তুলনায় পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সকল জেরেমিয়ার উচ্চবাচ্য যে ব্যর্থ, এ সত্য পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে।
ফরাসি সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসি সাহিত্যের ধর্ম। আমি পূর্বে বলেছি যে, ফরাসি সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স এবং আর্ট দুইই আছে। ফরাসি মনের এই প্রসাদগুণপ্রিয় তার ফলে সে দেশের দর্শন-বিজ্ঞানের ভিতরও সাহিত্যরস থাকে। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসি লেখকেরাই দিতে পারেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চাতেও ফরাসি পণ্ডিতদের সামাজিক বুদ্ধি ও রসজ্ঞান নষ্ট হয় না। প্রকৃত দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক কেবলমাত্র নিজের ব্যবহারের জন্য সত্য আবিষ্কার করতে ব্রতী হন না। মানবজাতির নিকট সত্য প্রকাশ ও প্রচার করাই তার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সত্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা পরিষ্কার করে অপরকে দেখিয়ে দেওয়া বুঝিয়ে দেওয়া, যা জটিল তাকে সরল করা, যা কঠিন তাকে সহজ করা তার পক্ষে একান্ত কর্তব্য। এক কথায় সায়েন্টিস্টের পক্ষে আর্টিস্ট, জ্ঞানীর পক্ষে গুণী হওয়া আবশ্যক। জর্মান পণ্ডিতদের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যায় ফরাসি পণ্ডিতেরা কত শ্রেষ্ঠ গুণী। জর্মান পণ্ডিতেরা অসাধারণ পরিশ্রম করে যা প্রস্তুত করেন তা অধিকাংশ সময়ে বিদ্যার গ্যাস বই আর কিছুই নয়। অপর পক্ষে ফরাসি পণ্ডিতেরা মানবজাতির চোখের সুমুখে যা ধরে দেন, সে হচ্ছে গ্যাসের আলো। বর্তমান ইউরোপের সর্ব প্রধান দার্শনিক বের্গস-র গ্রন্থসকলের সঙ্গে যার সাক্ষাৎপরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, সেসকল গ্রন্থ কাব্য হিসাবেও সাহিত্যের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে পারে। বের্গস-র দর্শন অতি কঠিন, কিন্তু তার রচনা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি উজ্জ্বল। দার্শনিকজগতের এই অদ্বিতীয় শিল্পীর হাতে গদ্যরচনা অপূর্ব চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। মণিকার যেমন রত্নের সঙ্গে রত্নের যোজনা করেন, বের্গসঁও তেমনি পদের সঙ্গে পদের যোজনা করেন। চিন্তারাজ্যের এই ঐন্দ্রজালিকের লেখনীর মুখে বশীকরণমন্ত্র আছে। এই স্বচ্ছতা এই উজ্জ্বলতার বলেই ফরাসি সাহিত্য যুগে যুগে ইউরোপের অপরাপর সাহিত্যের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে। আলোর ধর্ম এই যে, তা দিগদিগন্তে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং সকল দেশকেই নিজের কিরণে উদ্ভাসিত করে তোলে। এই কারণেই আমি পূর্বে বলেছি, ফরাসি সভ্যতার নির্বাণের সঙ্গেসঙ্গেই মানবের মনোজগতের আলো নিবে যাবে।
২.
এ স্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, ফরাসি সভ্যতার অধঃপতন হলেও তার পূর্বকীর্তি সবই বিশ্বমানবের জন্য সঞ্চিত থাকবে, অতএব সে সভ্যতার বিনাশে পৃথিবীর এমন কি ক্ষতি হবে। এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, এতে পৃথিবীর যে ক্ষতি হবে তা ইউরোপের অপর কোনো জাতি পূরণ করতে পারবে না। এ মতের সপক্ষে হেরি জেমসের আর-একটি কথা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেন যে, ফরাসি ইতিহাস ও ফরাসি সাহিত্য বিশ্বমানবকে এ আশা করতে শিখিয়েছে যে, ফরাসি সভ্যতা যুগে যুগে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, এবং এ আশা ভঙ্গ করলে ফ্রান্সের পক্ষে মানবজাতির নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তাঁর নিজের কথা এই–
And we have all so taken them from her, so expected them from her as our right, to the point that she would have seemed positively to fail of a passed pledge to help us to happiness if she had disappointed us, this lias been because of her treating us to the impression of genius as no niation since the Greeks has treated the watching world and because of our feeling that genius at that intensity is infallible.
সম্প্রতি কোনো কোনো জর্মান প্রফেসার বর্তমান জর্মান জাতির পক্ষ থেকে প্রাচীন গ্রীক জাতির জিনিয়াসের উত্তরাধিকারের দাবি করেছেন; কিন্তু এ দাবি উক্ত জর্মান প্রফেসার সম্প্রদায় ব্যতীত পৃথিবীর অপর কোনো জাতিই মঞ্জুর করেন নি। অপর পক্ষে ফরাসি জাতির জিনিয়াস যে অদম্য, ফন্ ঝুলল। Von Bulow প্রভৃতি জর্মান রাজমন্ত্রীরাও তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।
জিনিয়াস শব্দের সংস্কৃত প্রতিবাক্য হচ্ছে প্রতিভা। কিন্তু এই প্রতিভা শব্দের অর্থ নিয়ে বিষম মতভেদ আছে। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে প্রতিভার অর্থ নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। এ অর্থে ফরাসি জাতি যে অপূর্ব প্রতিভাশালী, তার প্রমাণের জন্য বেশি দূর যাবার দরকার নেই। গত শত বৎসরের ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি ভোগ করে নি। এই এক শ বৎসরের মধ্যে অন্তবিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ফ্রান্স বারংবার পীড়িত ও বিধ্বস্ত হয়েছে, অথচ এই অশান্তি এই উপদ্রবের ভিতরেও ফ্রান্স মানবজীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই তার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাস্তুর এবং দর্শনের ক্ষেত্রে বের্গসঁ যুগ প্রবর্তক মহাপুরুষ। আর সাহিত্যক্ষেত্রে হিউগো এবং মুস্সে Musset, গোতিয়ে Gautier এবং ভের্লেন Vorlaine প্রমুখ কবির, রেনাঁ Renan এবং তেইন Taine প্রমুখ সমালোচকের, স্তদাল Stendlial এবং বালজাক, ফ্লোবেয়র এবং মোপাসাঁ, লোতি Loti এবং আনাতোল ফ্রাঁস প্রমুখ উপন্যাসকারের, বোস্ত। Rostand এবং ব্রিয় Brieux প্রমুখ নাটককারের নাম ইউরোপের শিক্ষিতসমাজে কার নিকট অবিদিত? এঁরা সকলেই কাব্যজগতের নব পথের পথিক, নব বস্তুর স্রষ্টা। এবং এঁদের রচিত সাহিত্য যতই নতুন হোক, এক ফ্রান্স ব্যতীত অপর কোনো দেশে তা রচিত হতে পারত না; কেননা এসকল কাব্যকথা আলোচনার ভিতর থেকে একমাত্র। ফরাসি প্রতিভাই ফুটে উঠেছে। এ সাহিত্য সম্পূর্ণ নতুন হলেও বিজাতীয় নয়, পূর্বপূর্ব যুগের ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে এর রক্তের যোগ আছে। ফরাসি প্রতিভা যে কি পরিমাণে অদম্য, দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে সাহিত্যে এইসকল নব কীর্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অপর পক্ষে জর্মানির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কি দেখতে পাই? উনবিংশ শতাব্দী সাংসারিক হিসাবে জর্মানির সত্যযুগ। এই শত বৎসরের মধ্যে জর্মানি বাণিজ্যে ও সাম্রাজ্যে, বাহুবলে ও অর্থবলে অসাধারণ অ্যুদয় লাভ করেছে। কিন্তু এই অ্যুদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই তার কবিপ্রতিভা তার দার্শনিক বুদ্ধি অন্তর্হিত হয়েছে, গ্যেটে-শিলার-কান্ট-হেগেলের বংশ লোপ পেয়েছে। সে দেশে এখন যা আছে সে হচ্ছে ষষ্টি সহস্র বালখিল্য প্রফেসার। এরা সকলেই জ্ঞানরাজ্যের মুটে-মজুর, কেউ রাজা-মহারাজা নয়।
৩.
ফরাসি সাহিত্যের বিশেষ ধর্মটি যে কি, আজকে এ সভায় আমি সংক্ষেপে তারই পরিচয় দিতে চাই।
বর্তমান ইউরোপের দুটি সর্ব প্রধান সাহিত্য হচ্ছে ইংরেজি ও ফরাসি। ইউরোপের অপর কোনো দেশের সাহিত্য ঐশ্বর্যে ও গৌরবে এই দুই সাহিত্যের সমকক্ষ নয়।
ইংরেজি সাহিত্যের সহিত আমাদের সকলেরই যথেষ্ট পরিচয় আছে। সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যের সহিত ফরাসি সাহিত্যের পার্থক্যের পরিচয় লাভ করতে পারলে আমরা ফরাসি সাহিত্যের বিশেষত্বের সন্ধান পাব।
এক কথায় বলতে গেলে ইংরেজি সাহিত্য রোমান্টিক এবং ফরাসি সাহিত্য রিয়ালিস্টিক।
রিয়ালিজুম এবং রোমান্টিসিজম বলতে ঠিক যে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে সাহিত্যসমাজে বহুকালাবধি বহু তর্কবিতর্ক চলে আসছে। কিছুদিন হল বাংলা সাহিত্যেও সে আলোচনা শুরু হয়েছে।
আজকের এ প্রবন্ধে সে আলোচনার স্থান নেই, তবে সাহিত্যের এ দুই মার্গের মোটামুটি লক্ষণগুলি নির্দেশ করা কঠিন নয়।
রোমান্টিক সাহিত্যের প্রথম লক্ষণ এই যে, তা সাবজেটিভ। রোমান্টিক কবি প্রধানতঃ নিজের হৃদয়ের কথাই বলেন; নিজের সুখদুঃখ, নিজের আশানৈরাশ্য, নিজের বিশ্বাস-সংশয়, এইসকলই হচ্ছে তার কাব্যের উপাদান ও সম্বল। শুধু তাই নয়, খুঁটি রোমান্টিকের কাছে তার ব্যক্তিত্ব হচ্ছে জগতের সার সত্য। বাংলার সর্বপ্রথম কবি চণ্ডীদাসের কবিতা আগাগোড়া সাবজেটিভ, অপর পক্ষে সংস্কৃত কবিতা আগাগোড়া অবজেটিভ। এক ভর্তৃহরি ভিন্ন অপর কোনো সংস্কৃত কবি মানবহৃদয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে ‘অহং জানামি’ এ কথা বলেন নি। সংস্কৃতের ন্যায় ফরাসি সাহিত্যও প্রধানতঃ অবজেটিভ, বাহঘটনা ও সামাজিক মন নিয়েই ফরাসি সাহিত্যের আসল কারবার; এক কথায় ফরাসি জাতির দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষা বহিদৃষ্টি এবং অন্তদৃষ্টি ঢের বেশি তীক্ষ্ণ ও প্রখর। সে চোখ মানুষের ভিতর-বাহির দুই সমান দেখতে পায়।
রোমান্টিক সাহিত্যের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, সে সাহিত্য আধ্যাত্মিক। আমাদের দর্শনে সত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এক ব্যবহারিক, আরএক তদতিরিক্ত। ফরাসি সাহিত্যে এই ব্যবহারিক সত্যেরই আলোচনা ও চর্চা হয়ে থাকে। যা ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর যা বুদ্ধির অগম্য, ফরাসি সাহিত্যে তার বড়-একটা সন্ধান পাওয়া যায় না। The proper study of mankind is man, এই হচ্ছে ফরাসি-মনের মূল কথা। সুতরাং মানবসমাজ মানবমন ও মানবচরিত্রের জ্ঞানলাভ করা ও বর্ণনা করাই ফরাসি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ জ্ঞান লাভ করতে হলে সামাজিক মানবের আচারব্যবহার লক্ষ্য করতে হয়, এবং সেই সঙ্গে সেই আচারব্যবহারের আবরণ খুলে ফেলে তার আসল মনের পরিচয় নিতে হয়; তাও আবার সমগ্রভাবে নয়, বিশ্লেষণ করে, পরীক্ষা করে। বৈজ্ঞানিক যে ভাবে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে জড়বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করেন, ফরাসি সাহিত্যিকরাও সেই ভাবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানবতত্ত্ব নির্ণয় করেন। তারা মানবজাতিকে চরিত্র অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, মানবের কার্যকারণের আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী ও যোগাযোগ আবিষ্কার করতে চান। এই কারণে Moliere মোলিয়েরের নাটক ফরাসি প্রতিভার সর্বোচ্চ নিদর্শন। মোলিয়ের ধর্মের আবরণ খুলে পাপের, বিদ্যার আবরণ খুলে মূখতার, বীরত্বের আবরণ খুলে কাপুরুষতার, প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্তি পৃথিবীর লোকের চোখের সুমুখে খাড়া করে দিয়েছেন। কিন্তু এসকল মূর্তি দেখে মানুষের মনে ভয় হয় না, হাসি পায়। মানুষের ভিতর যা-কিছু লজ্জাকর আর হাস্যকর, তাই মোলিয়েরের চোখে পড়েছে, আর যা তাঁর চোখে ধরা পড়েছে তাই তিনি অপরের নিকট ধরিয়ে দিয়েছেন।
ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটককারের সঙ্গে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটককারের তুলনা করলেই এ উভয়ের প্রতিভার পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষিত হবে। শেক্সপীয়রের রিচার্ড দি থার্ড, ইয়াগো প্রভৃতির পরিচয়ে দর্শকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। শাইলক আমাদের মনে যুগপং করুণা ও ঘৃণার উদ্রেক করে, কিং লিয়রের পাগলামি আমাদের মনকে বেদনা দেয়, এয়ারিয়েল Aeriel আমাদের স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়। ফরাসি কবিরা শুধু হাস্য ও করুণ, বীর ও মধুর রসের চর্চা করেন। ইংরেজ কবিদের ন্যায় তারা ভয়ংকর ও অদ্ভুত রসের রসিক নন। ফরাসি জাতির ভিতর কোনো শেপীয়র জন্মায় নি ও জন্মাতে পারে না। পাগল প্রেমিক ও কবি যে এক জাত, এ কথা কোনো ফরাসি কবি বলেনও নি, স্বীকারও করেন নি। কেননা তারা তাদের সংসারজ্ঞান ও তাদের শিক্ষিত ও মার্জিত বুদ্ধির উপরেই চিরকাল নির্ভর করে এসেছেন। ফরাসি জাতির দেহে কিংবা মনে কোনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই এবং তারা কস্মিনকালেও তাদের মগ্নচৈতন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। এই কারণে ফরাসি কবিতা ইংরেজি কবিতার তুলনায় আবেগহীন ও কল্পনার ঐশ্বর্যে বঞ্চিত; সে কবিতা মানবমনের গভীরতম দেশ স্পর্শ করে না।
৪.
অপর পক্ষে এই সচেতন সচেষ্ট মনের উপর নির্ভর করায় ফরাসি গদ্যসাহিত্য যে শক্তি ও তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে ইংরেজি গদ্যসাহিত্যে সে শক্তি সে তীক্ষ্ণতা নেই। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের মন সামাজিক, সুতরাং ব্যবহারিক সত্যের সঙ্গেই তাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে। সেই পরিচিত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলে মানবমনের নিকট ফরাসি সাহিত্য এত সহজবোধ্য, এত বহুমূল্য। ইংরেজি কবিতা মানুষের মনকে উত্তেজিত উদ্দীপিত করে, সে মনকে জ্ঞানবুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়ে কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। সে কবিতার মোহ আমাদের মনকে চিরদিনের মত অভিভূত করে রাখতে পারে না, আমরা আবার এই মাটির পৃথিবীতে দিনের আলোয় ফিরে আসি। এ কবিতার রেশ যে মনের উপর থেকে যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং তার ফলে আমাদের হৃদয়মন যুগপৎ গভীরতা ও উদারতা লাভ করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ সামাজিক মনই আমাদের চিরদিনের মন, আর ঐ বুদ্ধিবৃত্তিই আমাদের চিরজীবনের সহায়। ফরাসি সাহিত্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মাজিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করে। সে সাহিত্য মানুষকে দেবতা হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করে। অতএব সে সাহিত্য আমাদের মনে মানুষের প্রতি, ভক্তির না হোক, প্রীতির উদ্রেক করে। কেননা তার চর্চায় আমরা স্বজাতিকে চিনতে ও বুঝতে শিখি, এবং সেই সঙ্গে আমরা ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা, গোঁড়ামি আর হাবড়ামি, মানসিক আলস্য ও জড়তা, হয় পরিহার করতে নয় গোপন করতে শিখি। ফরাসি সাহিত্য মানুষকে দেবতা নয়, সুসভ্য করে তোলে। ফরাসি সাহিত্য সকল প্রকার মিথ্যার সকল প্রকার কপটতার প্রবল শত্রু এবং ফরাসি-মনের এই নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসা সে সাহিত্যের সর্বপ্রধান গুণ। এই কারণেই ফরাসি প্রতিভা ইতিহাসে জীবনচরিতে সামাজিক উপন্যাসে এত ফুটে উঠেছে। এবং এই একই কারণে ফরাসি সমালোচকদের তুল্য সমালোচক পৃথিবীর অপর কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করে নি। এবং ফরাসি সমালোচনার বিষয় কেবলমাত্র সাহিত্য নয়, সমগ্র মানবজীবন। ধর্মনীতি রাজনীতি সমাজ সভ্যতা এসকলই ফরাসি জাতির হস্তে যুগে যুগে পরীক্ষিত হয়ে আসছে।
অনেকের ধারণা যে, জোলার নভেলই হচ্ছে ফরাসি রিয়ালিজমের চূড়ান্ত উদাহরণ। এ কথা সত্য যে, সত্যের অনুসন্ধানে মনোরাজ্যের হেন দেশ নেই যেখানে ফরাসি লেখকেরা যেতে প্রস্তুত নন, সে দেশ যতই অপ্রীতিকর ও যতই অসুন্দর হোক; এবং সত্যের খাতিরে হেন কথা নেই, যা তারা বলতে প্রস্তুত নন, সে কথা যতই অপ্রিয় যতই অবক্তব্য হোক। কিন্তু আমি রিয়ালিজম শব্দ জোলার অনুমত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করি নি। লোকে সচরাচর যাকে আইডিয়ালিম বলে থাকে তাও আমার ব্যবহৃত রিয়ালিজম শব্দের অন্তভূত। মানবমন মানবজীবনের উপর আলো ফেলে যা দেখা যায় তাই হচ্ছে ফরাসি সাহিত্যের বিষয়। বলা বাহুল্য, সে আলোয় অনেক সুন্দর, অনেক কুৎসিত, অনেক মহৎ, অনেক ইতর মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। যা হেয় তাও যেমন সত্য, যা উপাদেয় তাও তেমনি সত্য। এর ভিতর কোন্ শ্রেণীর সত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তা লেখকের ব্যক্তিগত রুচি ও দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সুতরাং আইডিয়ালিজুম এবং রিয়ালিজম সাহিত্যে পাশাপাশি দেখা দেয়। ফরাসি লেখকেরা মানবের অন্তরে এমন এক-একটি মূল প্রবৃত্তির আবিষ্কার করতে চান, অপর প্রবৃত্তিগুলি যার বিবাদী সংবাদী অনুবাদী সুর মাত্র। সুতরাং একই মনোভাব থেকে ফরাসি সাহিত্যে মানবের আইডিয়ালিস্টিক এবং রিয়ালিস্টিক উভয় চিত্রই অঙ্কিত হয়ে থাকে। প্রাচীন ফরাসি সাহিত্যে মানবসমাজের আইডিয়ালিস্টিক চিত্র বিরল নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জোলা প্রভৃতি রিয়ালিস্টগুণ যে অতিমাত্রায় কদর্যতার চর্চা করেন, সে কতকটা ভিক্তর হিউগো প্রভৃতি রোমান্টিক লেখকদের প্রতিবাদস্বরূপে। আর-এক কথা, আমার সহিত যত ফরাসি লেখকের পরিচয় আছে, আমার বিশ্বাস, তার মধ্যে এক জোলার গ্রন্থই বিশেষরূপে ফরাসি-ধর্মে বঞ্চিত; জোলার রচনায় ফরাসিসুলভ লিপিচাতুর্য নেই; জোলার মন সূর্যকরোজ্জ্বল নয়, সে মন নিশাচর; জোলা মানুষকে দেবতা হিসেবে দেখেন নি, মানব হিসেবেও দেখেন নি, তার চোখে আমরা সকলেই ছদ্মবেশী দানব। প্রকৃত পক্ষে জোল। ফরাসি লেখক নন, তিনি ছিলেন জাতিতে ইতালিয়ান।
ফরাসি সাহিত্যের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে তার আর্ট। ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন
The one high principle which, througlı so many generations, lias guided like a star the writers of France is the principle of deliberation, of intention, of a conscious search for ordered beauty; an unwavering, an indomitable pursuit of the endless glories of art. (Lytton Strachey, Landmarks in french Literature, Home University Library) এই আর্টের গুণেই ফরাসি রচনা আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে।
এক কথায় এ আর্ট রোমান্টিক নয়, ক্ল্যাসিকাল। কি কি গুণের, কি কি লক্ষণের সভাবে রচনা আর্ট হয়, সে বিষয়ে ফরাসি জাতির মত নিম্নে বিবৃত করছি। ফরাসি রচনার রীতির পরিচয় দেবার পূর্বে ফরাসি ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, কেননা ভাষার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, এত ঘনিষ্ঠ যে এ কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে, সকল দেশের জাতীয় সাহিত্যের রূপগুণ সেই দেশের ভাষার শক্তির উপর নির্ভর করে। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জাতীয় সাহিত্য রচিত হবার বহু পূর্বে জাতীয় ভাষা গঠিত হয়। যুগযুগান্তরের আত্মপ্রকাশের চেষ্টার ফলে একটি জাতীয় ভাষা গড়ে ওঠে এবং সেই ভাষার অঙ্গে জাতীয় মনের ছাপ থেকে যায় এবং তার অন্তরে জাতীয় চরিত্র বিধিবদ্ধ হয়ে থাকে।
ভাষার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ ফরাসি ল্যাটিনের অপভ্রংশ অথবা প্রাকৃত। ফরাসি ভাষার শব্দসমূহ ল্যাটিন হতে উদ্ভূত। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষায় যাকে তদ্ভব বলে, ফরাসি অভিধানের প্রায় সকল শব্দই সেই শ্রেণীভুক্ত, এসকলই ল্যাটিনের তদ্ভব। এ ভাষায় দেশি এবং বিদেশি শব্দের সংখ্যা এত অল্প যে, তা নগণ্য স্বরূপে ধরা যেতে পারে। ফরাসি ভাষা মূলতঃ এক হওয়ার দরুন এ ভাষার ভিতর এমন-একটি ঐক্য ও সমতা আছে যা রচনার একটি বিশেষ রীতি গড়ে তোলার পক্ষে একান্ত অনুকূল। ইংরেজি ভাষা ঠিক এর বিপরীত। অ্যাংলো-স্যাশন এবং নর্মান-ফ্রেঞ্চ, এই দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে বর্তমান ইংরেজি ভাষার উৎপত্তি। এর ফলে সে ভাষার অন্তরে বৈচিত্র্য আছে, সমতা নেই। ইংরেজি রচনার-যে কোনো-একটি বিশিষ্ট রীতি নেই, ইংরেজি ভাষার বর্ণসংকর তার অন্যতম কারণ; ইংরেজি লেখকেরা যে প্রত্যেকেই নিজের রুচি অনুসারে রচনার স্বতন্ত্র রীতি গড়ে নিতে পারেন, তার প্রচুর এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ এক উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্য হতে পাওয়া যায়। কার্লাইল এবং নিউম্যান, রাকিন এবং ম্যাথু আর্নল্ড, থ্যাকারে এবং মেরেডিথ, ওয়ার্ডওয়ার্থ এবং শেলি, টেনিসন এবং ব্রাউনিং— একই যুগে এইসকল বিভিন্নপন্থী লেখকের আবির্ভাব এক ইংলণ্ড ব্যতীত অপর কোনো দেশে সম্ভব হত না। উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সের রোমান্টিক এবং রিয়ালিস্টিক লেখকদের রচনার ভিতর এরূপ জাতিগত প্রভেদ নেই। ফরাসি ভাষায় এরূপ বৈচিত্র্যের অবসর নেই। সুতরাং ফরাসি লেখকেরা যুগে যুগে রচনার, বৈচিত্র্য নয়, ঐক্যসাধন করে একটি আদর্শ রীতি গড়ে তোলবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করেছেন, এবং সে বিষয়ে কৃতকার্য হয়েছেন। এই যুগযুগান্তরের সাধনার ফলে অধিকাংশ ফরাসি শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ ভাষার ব্যবহারে অশিক্ষিতপটুত্ব লাভ করবার জো নেই। আমাদের দেশের বাধা ঠাটের বাঁধা রাগিণীর মত এ ভাষা গুণীব্যক্তির হাতেই পূর্ণশ্রী লাভ করে, এবং তার মূর্তি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একটি, বেপর্দায় হাত পড়লে সুর যেমন আগাগোড়া বেসুরো হয়ে যায়, তেমনি একটি অসংগত কথার সংস্পর্শে ফরাসি রচনা আগাগোড়া অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিমিত শব্দে স্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করবার পক্ষে এ ভাষা যতটা অনুকূল, হৃদয়ের গভীর ও অস্পষ্ট মনোভাব প্রকাশের পক্ষে তাদৃশ অনুকুল নয়। এর ফলে গদ্যরচনার পক্ষে ফরাসি হচ্ছে ইউরোপের আদর্শ ভাষা।
ভাষা হচ্ছে সাহিত্যের উপাদান, কিন্তু কেবলমাত্র উপাদানের গুণে কোনো শিল্পই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে না, যদি না তা শিল্পীর হাতে পড়ে। আর তা ছাড়া অন্যান্য শিল্পের উপাদানের সঙ্গে সাহিত্যের উপাদানের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে।
পাষাণ কি ধাতু, বর্ণ কি স্বর, আমরা বাইরে থেকে যা পাই তাই আমাদের গ্রাহ্য করে নিতে হয়, কেননা ওসকল বাহজগতের বস্তু; আমরা তা সৃষ্টি করি নি, অতএব আমরা তার ধাতও বদলে দিতে পারি নে। কিন্তু। ভাষা হচ্ছে আমাদেরই সৃষ্টি। সুতরাং পূর্বপুরুষদের নিকট যে ভাষা আমরা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে লাভ করি, তার অল্পবিস্তর রূপান্তর করা আমাদের সাধ্যের অতীত নয়। আমরা যা পড়ে পাই তা চৌদ্দ আনা, তাকে ষোলো আনা করা -করা, সে আমাদের হাত। বর্তমান ফরাসি ভাষা এবং প্রাচীন ফরাসি ভাষা এই দুই মূলতঃ এক হলেও এ দুইয়ের ভিতর প্রভেদ বিস্তর। যুগের পর যুগের ফরাসি লেখকদের যত্নে ও চেষ্টায় এ ভাষা জাতীয় মনোভাব প্রকাশের এমন উপযোগী যন্ত্র হয়ে উঠেছে। ফরাসী ভাষার এ ইভলিউশন আপনি হয় নি, এ উন্নতি এ পরিণতির ভিতর ফরাসি জাতির সুবুদ্ধি ও সুরুচি, যত্ন ও অধ্যবসায়, এসকলেরই সমান পরিচয় পাওয়া যায়।
৬.
যেদিন থেকে ফরাসি জাতির ধারণা হল যে, সাহিত্যরচনা করা একটি আর্ট, সেইদিন থেকে ফরাসি লেখকেরা কিসে রচনা সুগঠিত হয়, সে বিষয়েও পুরো লক্ষ্য রেখে আসছেন। কি যে আর্ট আর কি যে আর্ট নয়, সে বিষয়ে অদ্যাবধি বহু মতভেদ আছে। সৌন্দর্যের অর্থ যে কি, সে বিষয়ে দার্শনিক তর্কের আর শেষ নেই। তবে আমাদের সহজ মন এবং সাদা চোখ দিয়ে বিচার করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা যাকে বস্তুর রূপ বলি তা অনেক পরিমাণে তার আকারের উপর নির্ভর করে। অন্ততঃ আমরা বাঙালিরা যা কদাকার তাকে সুন্দর বলি নে। মানবমনের এই সহজ প্রকৃতির উপরেই ফরাসি জাতির রচনার আর্ট প্রতিষ্ঠিত। কিসে রচনার অঙ্গসৌষ্ঠব হয় সে বিষয়ে ফরাসি মনীষীরা বহু চিন্তা বহু বিচার করে গেছেন, এবং সেই চিন্তা সেই বিচারের ফলে ফরাসি রচনা এত সাকার, এত পরিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছে।
আমি প্রথমেই বলেছি যে, খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ফরাসী সাহিত্য জন্মলাভ করে; প্রথম তিন শত বৎসরের ফরাসি সাহিত্য আর্টহীন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণচণ্ডী যেমন আর্টহীন, রোমা দ্য রোলা, রোমা দ্য রোজ প্রভৃতি ফ্রান্সের জাতীয় মহাকাব্যও সেইরূপ আর্টহীন। এই যুগের লেখকদের শব্দের নির্বাচন ও পদের যোজনার প্রতি কোনোই লক্ষ্য ছিল না।
তার পর খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফরাসি জাতি যখন প্রাচীন গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যের পরিচয় লাভ করলে, তখন হতে লেখা জিনিসটে যে একটি আর্ট এ বিষয়ে ফরাসি কবি এবং ফরাসি গদ্য-লেখকের সজ্ঞান হয়ে উঠল। এই ক্ল্যাসিক-সাহিত্যের আদর্শ ফরাসি লেখকদের নিকট একমাত্র আদর্শ হয়ে উঠল এবং এই কারণেই ক্ল্যাসিসিজম হচ্ছে সে সাহিত্যের সর্বপ্রধান ধর্ম।
৭.
দুই উপায়ে ভাষার রূপান্তর করা যায় : এক, শব্দের যোগের দ্বারা, আরএক, বিয়োগের দ্বারা। ফরাসি লেখকের বর্জনের সাহায্যেই ভাষার সংস্কার করেন। খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মালেব Malherbe নামক জনৈক কবি এই ভাষা-সংস্কারকার্যে ব্রতী হন। তিনি প্যারি নগরীর মৌখিক ভাষাই সাহিত্যরচনার আদর্শভাষাস্বরূপে গণ্য করেন। কেননা সে ভাষার ভিতর এমন-একটি ঐক্যসমতা প্রসাদগুণ এবং ভদ্রতা ছিল, যা কোনো প্রাদেশিক ভাষার অন্তরে ছিল না। এই কারণে সাহিত্য হতে প্রাদেশিক শব্দসকল বহিষ্কৃত করে দেওয়াই তার মতে হল ভাষাসংস্কারের সর্বপ্রথম এবং সর্ব প্রধান উপায়। মালের্বের মতে এক দিকে যেমন প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহারে কুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়, অপর দিকে সাহিত্যে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারেও তেমনি কুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়। এক কথায়, গ্রাম্যতা ও পাণ্ডিত্য, এই দুইই কাব্যের ভাষায় সমান বর্জনীয়। কেননা সে যুগের ফ্রান্সের ভদ্রসমাজের মতে নিরক্ষর লোকের ভাষা ও পুঁথিগত বিদ্যার ভাষা এই দুইই সমান : ইতর বলে গণ্য হত। দুয়ের ভিতর পার্থক্য এই যে, এর একটি লজ্জার, অপরটি হাস্যের উদ্রেক করে। এই মত ফ্রান্সের লেখকসমাজে গ্রাহ্য হয়েছিল, কেননা তাদের মতে প্রাচীন ফরাসি সাহিত্যের ভাষা এক ভাষা নয়, একটা জোড়াতাড়া দেওয়া ভাষা। এর ফলে রাবলে Rabelais প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের পাঁচরঙা ভাষার পরিবর্তে ফরাসি গদ্যের ভাষা একরঙা হয়ে উঠল।
উপাদান নির্বাচন হচ্ছে শিল্পীর প্রথম কাজ, কিন্তু সেই উপাদানে মূর্তি গঠন করাই তার আসল কাজ। সুতরাং মালেব প্রমুখ সমালোচকেরা পদনির্বাচনের ন্যায় পদযোজনার প্রতিও লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা পদের সঙ্গে পদের যোজনা করে বাক্যগঠন করি এবং বাক্যের সঙ্গে বাক্যের যোজনা করে একটি কবিতা কিংবা প্রবন্ধ রচনা করি। সুতরাং বাক্য এবং রচনা যাতে সুগঠিত হয় সে বিষয়ে ফরাসি লেখকেরা এই যুগ থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি সমান মনোনিবেশ করে আসছেন। এ গঠনে যাতে রেখার সুষমা থাকে সামঞ্জস্য থাকে, রচনার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাতে যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত। হয়, এবং পরস্পরের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ হয়, যাতে করে একটি রচনা পূর্ণাবয়ব সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সমগ্র হয়ে ওঠে–এই হচ্ছে ফ্রান্সের সাহিত্যশিল্পীর যুগযুগের সাধনার ধন। রচনার দেহ সুগঠিত করবার জন্য সকল প্রকার বাহুল্য বর্জন করা আবশ্যক। যারা রাগ আলাপ করেন, চিকারির ঝন্ঝনানি তাদের কানে অসহ্য। খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বোয়ালো Boileau নামক বিখ্যাত সমালোচক বিশেষ করে রচনার অমার্জনীয় দোষের সম্বন্ধে সমাজের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিলেন। ভাষার কৃত্রিমতা, বৃথা বাগাড়ম্বর, উপমার আতিশয্য, অনুপ্রাসের ঝংকার প্রভৃতি রচনার দোষের প্রতি তিনি চিরজীবন ধরে এমন তীক্ষ্ণ, এমন অজস্র বাণ বর্ষণ করেছিলেন যে, ফরাসি সাহিত্য হতে সকল প্রকার অত্যুক্তি ও অতিবাদ, কষ্টকল্পনা ও অবোধ পাণ্ডিত্য চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হয়েছে।
রচনাকে শব্দাড়ম্বরে গৌরবান্বিত, শব্দালংকারে ঐশ্বর্যবান, পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগে মর্যাদাপন্ন এবং বাচালতায় সমৃদ্ধিশালী করবার লোভ সংবরণ করা যে কি কঠিন, তা লেখক মাত্রই জানেন। ফরাসি লেখকেরা এই সংযম নিজেরা অভ্যাস করেন এবং অপরকে অভ্যাস করতে শিক্ষা দেন। পূর্বোক্ত ফরাসি আলংকারিক কর্তৃক প্রদর্শিত সাহিত্যের ত্যাগমার্গ ফরাসি লেখকেরা যে কেন অবলম্বন করেছিলেন, তার একটু বিশেষ কারণ আছে। প্যাকাল, লা ব্রুইয়ের La Bruyere, বয়ে Bossuet, ফেনেল Fenelon, রাসীন Racine, মোলিয়ের প্রভৃতি সে যুগের ফ্রান্সের প্রথম শ্রেণীর গদ্যপদ্যলেখক মাত্রেই মালের্ব কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং বোয়ালো কর্তৃক পরিষ্কৃত রচনার এই নব পথ অবলম্বন করেই সাহিত্যজগতে অমর হয়েছেন। এরা যে বিনা অপত্তিতে এই নব আলংকারিক মত গ্রাহ্য করেছিলেন, তার কারণ তারা যেসকল মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন রচনার এই নবপদ্ধতি সে মনোভাব প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। সে যুগের ফরাসি মনোভাবের পূর্ণ পরিচয় Descartes দেকার্তের দর্শনে পাওয়া যায়। সেই দর্শনে ফরাসি প্রতিভা তার আত্মজ্ঞান লাভ করে। আপনারা অনেকেই জানেন যে, যে-আইডিয়া সুস্পষ্ট পরিচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্ট, তাই হচ্ছে দেকার্তের মতে সত্যের পরিচায়ক। অর্থাৎ যে জ্ঞান আমাদের জাগ্রত বুদ্ধির আয়ত্তাধীন, এবং যা ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। এবং দেকার্তের মতে একমাত্র অন্তদৃষ্টির সাহায্যেই এই শ্রেণীর সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ফরাসি লেখকেরা মানবমনের ও মানবচরিত্রের সেই সত্য আবিষ্কার করতে এবং প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, যা জ্ঞানের আলোকে সুস্পষ্ট হবে, যা ন্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এক কথায়, তারা reasonকে দেবতা করে। তুলেছিলেন, এবং reasonable মনোভাব প্রকাশের পক্ষে যে সুসংযত সুসংহত এবং সুশৃঙ্খল ভাষাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? রিজুনেবল মনোভাব রিনেবল ভাষায় ব্যক্ত করার দরুন ফরাসি ক্ল্যাসিকাল লেখকেরা য়ুরোপের সাহিত্যসমাজে সর্বাগ্রগণ্য হয়ে উঠেছিলেন। এই কারণেই সে সাহিত্যের প্রভাব সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, ও সকল জাতির মন বশীভূত করে। দেশভেদে কালভেদে জাতিভেদে রিজুনের কোনো ভেদ হয় না, ও-বস্তু সর্বলোকসামান্য। ঐ হচ্ছে মনের একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে সকল মনের মিলন হতে পারে। মানুষ যদি সমবুদ্ধি হয়, তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহানুভূতি জন্মাতে বাধ্য। এই কারণেই হেরি জেম্স বলেন যে, ফরাসি জাতি lives for us। এমনকি, রোমান্টিক ইংলণ্ড এক শতাব্দীর জন্য স্বধর্ম ত্যাগ করে এই ফরাসি সাহিত্যের অধীনতা স্বীকার করেন। অ্যাডিসন এবং পোপ, লকী এবং হিউম, গিবন এবং গোল্ড সমিথ, সকলেই সাহিত্যের এই ফরাসি রীতিই অনুসরণ করেছিলেন। ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ল্যাসিসিজম ফরাসি ক্ল্যাসিসিজুমের অনুকরণ ব্যতীত আর কিছু নয়। ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবের সময় পর্যন্ত এই রীতি একাধিপত্য করে। ভল্টেয়ারের হাতে ফরাসি ভাষা এত লঘু আর এত তীক্ষ্ণ, এত চোস্ত এবং এত সাফ হয়ে উঠেছিল যে, তার পর সে রীতির আর ক্রমোন্নতি হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ভল্টেয়ারের ভাষাই তার চূড়ান্ত পরিণতি। ভাষার ধার এর চাইতে বাড়াতে গেলে যে পরিমাণ শান দিয়ে তার দেহ ক্ষয় করতে হয়, তাতে ভাষার দেহত্যাগ করতে হয়।
৮.
অপর সকল গুণকে উপেক্ষা করে একটিমাত্র গুণের অতিমাত্রায় চর্চা করলে কালক্রমে তা দোষ হয়ে দাঁড়ায়। এই সুমার্জিত ভাষা মানুষের চিন্তাপ্রকাশের জন্য যেমন উপযোগী, মানবহৃয়ের আকাঙ্ক্ষা-আকুলতা আশাভয় সংশয়-বিশ্বাস প্রভৃতি অনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশের জন্য তেমনি অনুপযুক্ত। ক্রমান্বয়ে ইতর গণ্যে শব্দের পর শব্দ বর্জন করে এ ভাষা অতিশয় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এ ভাষায় কোনোরূপ ছবি আঁকা অসম্ভব। কেননা যে শব্দের গায়ের রং আছে, সে শব্দ এ সাহিত্যিক ভাষা হতে বহিষ্কৃত হয়েছিল। যে শব্দের বস্তুর সঙ্গে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ সুস্পষ্ট, সেই শব্দই এ সাহিত্যে গ্রাহ্য হত। কিন্তু যে শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি আছে, অর্থাৎ যার অর্থের অপেক্ষা অনুরণন (suggestiveness) প্রবল, সে শব্দ এ সাহিত্যে উপেক্ষিত হত। ফরাসি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের পূর্বসভ্যতার সঙ্গেসঙ্গে তার পূর্বসাহিত্যের রীতিনীতিও মর্যাদাভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নবীন ফ্রান্সে রিজন তার দেবত্ব হারিয়ে বসেছিল। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের নূতন সাহিত্য ক্ল্যাসিসিজুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই সাহিত্যই রোমান্টিক বলে পরিচিত। শাতোব্রিয়। Chateaubriand এর প্রবর্তক, এবং ভিক্টর হিউগো এর নায়ক। ক্ল্যাসিসিজুমের ভাব ও ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই এ সাহিত্যের লক্ষণ ও বিশেষত্ব। রিজনের পরিবর্তে কল্পনা, বাঁধাবাঁধি নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, ভাষাপ্রয়োগে কৃপণতার পরিবর্তে অজস্রতা— রোমান্টিক সাহিত্যে এইসবই প্রাধান্য লাভ করেছিল। রোমান্টিক লেখকেরা ইতর বলে কোনো শব্দকেই বর্জন করেন নি, এদের প্রসাদে এক দিকে শত শত উপেক্ষিত পতিত ও বিস্মৃত শব্দ, অপর দিকে শিল্পবিজ্ঞান হতে সংগৃহীত শত শত পারিভাষিক শব্দ সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করলে। আমাদের নব্য আলংকারিক-মতে—
ন স শব্দো ন তদ্বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন স কলা
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ। (রুদ্রট-ধৃত বচন)
ফরাসি নব্য আলংকারিকদেরও এই একই মত। এর ফলে সাহিত্যের ভাষা আবার শব্দসম্পদে বিপুল ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠল। এই নূতন ভাষা হৃদয়ের আবেগ প্রকাশের জন্য যেমন উপযোগী, বাহিরের দৃশ্য অঙ্কনের জন্য তেমনি উপযোগী। এ রোমান্টিক সাহিত্য কিন্তু আসলে উচ্ছঙ্খল সাহিত্য নয়। ভিক্টর হিউগো, মুসসে প্রমুখ লেখকের মুখে অবাধ স্বাধীনতা প্রচার করলেও কাজে আর্টের অধীনতা হতে মুক্ত হন নি। এমনকি কোনো কোনো সমালোচকের মতে ভিক্টর হিউগো ফরাসি সাহিত্যের একজন অপূর্ব শিল্পী। তাঁর প্রতি ছত্রে কারিগরের হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসি রোমান্টিসিজম অনেকটা বক্তগত। এক কথায়, হিউগো প্রমুখ কবির। শুধু ভাষার পুষ্টিমার্গ অবলম্বন করেছিলেন, কেননা রোমান্টিক মনোভাব এ জাতির মনে কখনোই সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করতে পারে নি। মানুষের সমগ্ৰ মন তার বুদ্ধির চাইতে ঢের বড়, এবং যুক্তিতর্কের অপেক্ষা অনুভূতি টের বেশি নির্ভরযোগ্য, এই বিশ্বাসের উপরই যথার্থ রোমান্টিক সাহিত্য দাঁড়িয়ে থাকে। এই দৃষ্ট বিশ্বের পিছনে একটি অদৃষ্ট বিশ্ব আছে, মানবমনের এমন একটি ধর্ম আছে, যার গুণে এই নিগূঢ় বিশ্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়— এই হচ্ছে রোমান্টিক দর্শনের মূল কথা। আর যে বস্তু যুক্তিতর্কের সাহায্যে জানা যায় না, তা যুক্তিতর্কের সাহায্যে অপরকে জানানো যায় না; তাই রোমান্টিক কবিরা নিজে যা অনুভব করছেন, অপরকে তা অনুভব করাতে চান। এ স্থলে ভাষার অর্থের চাইতে তার ইঙ্গিতের মূল্য ঢের বেশি।
ফরাসি রোমান্টিক সাহিত্যের ভাষার প্রলেপ তুলে ফেললে দেখা যায় যে, তার ভিতর রোমান্টিসিজমের খাঁটি মাল নেই।
রোমান্টিসিজ্ম ফরাসি জাতির ধাতুগত নয়। সুতরাং ফরাসি মনের উপর এ জোর-করা সাহিত্যের প্রভাব চিরস্থায়ী হল না। এই রোমন্টিসিজমের প্রতিবাদ স্বরূপেই ফ্রান্সের নব রিয়ালিজম জন্মগ্রহণ করে। কল্পনার পরিবর্তে রিজন ফরাসি সাহিত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফরাসি রিয়ালিস্টরা তাদের জাতীয় বুদ্ধির অনুসরণ করে আবার সত্যের সন্ধানে বহির্গত হয়েছিল। এবং সে সত্য কুৎসিতই হোক আর বীভৎসই হোক, ফরাসি রিয়ালিস্টরা তার ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি। রোমান্টিক দল ফরাসি সাহিত্যকে যা দান করে গিয়েছে, সে হচ্ছে অগাদ শব্দসম্পদ। রিয়ালিস্টদের নেতা ফ্লোবেয়র সেই নূতন উপাদান নিয়েই পুরাতন রীতিতে সাহিত্য গঠন করেছেন। এর ফলে ক্লোবেয়র এবং তাঁর শিষ্য মোপাসাঁর ন্যায় শিল্পী জগতের সাহিত্যে দুর্লভ।
যে বিরাট সৌন্দর্যে মানুষের মনকে স্তম্ভিত অভিভূত করে, যে সৌন্দর্য অতিজগতের আলো ও ছায়ায় রচিত, সে সৌন্দর্য ইংরেজি সাহিত্যে আছে, ফরাসি সাহিত্যে নেই। কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্যে ফরাসি সাহিত্য অতুলনীয়।
আমি ফরাসি সাহিত্যের চর্চায় যে আনন্দ লাভ করেছি, সে আনন্দের ভাগ আপনাদের দিতে পারলুম না। সুতরাং সে সাহিত্য হতে যে শিক্ষা লাভ’ করেছি তারই পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি, যদি তাতে কৃতকার্য হয়ে থাকি, তাহলেই আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।
৯.
আমি চাই যে আমাদের শিক্ষিতসমাজে ফরাসি সাহিত্যের সম্যক্ চর্চা হয়। আমার বিশ্বাস, সে চর্চার ফলে আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে।
আমি বলেছি যে ইংরেজি সাহিত্য মুখ্যতঃ রোমান্টিক, এবং ফরাসি সাহিত্য মুখ্যতঃ রিয়ালিস্টিক। যে দুটি বিভিন্ন মনোভাব থেকে এই দুটি পৃথক্ চরিত্রের সাহিত্য জন্মলাভ করে, প্রতি জাতির মনে সে উভয়েরই স্থান আছে। কোন জাতি এর মধ্যে কোনটির উপর ঝোক দেন, তার উপরেই জাতীয় সাহিত্যের বিশেষত্ব নির্ভর করে।
প্রাক্ব্রিটিশ যুগের বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাই দুটি পৃথক্ ধারা বরাবর পাশাপাশি চলে এসেছে : একটি সম্পূর্ণ সাজেটিভ, অপরটি সম্পূর্ণ অবজেটিভ। যে বাঙালি জাতির মন থেকে বৈষ্ণব পদাবলী জন্মলাভ করেছে, সেই বাঙালি জাতির মন থেকেই কবিকঙ্কণচণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল জন্মলাভ করেছে। সুতরাং রোমান্টিক এবং রিয়ালিস্টিক উভয় সাহিত্যই আমাদের হৃদয়-মন সমান স্পর্শ করতে পারে। ইংরেজি সাহিত্য যেমন আমাদের মনের একটি দিক ফুটিয়ে তুলেছে, আমাদের মনের আর-একটি দিক আছে যা ফরাসি সাহিত্য তেমনি ফুটিয়ে তুলতে পারে।
ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সাহিত্যে যে কি সুফল জন্মেছে তা সকলেই জানেন; কিন্তু সেই সঙ্গে যে কি কুফল জন্মেছে তা সকলের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয়।
সংগীতের মত সাহিত্যও যে একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না, এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরেজি গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ। কেননা যে জাতির ক্ল্যাসিক্স ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয় হচ্ছে সংস্কৃত, সে জাতির পক্ষে রচনার আর্ট সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া স্বাভাবিক নয়।
একটি ইংরেজ লেখক বলেছেন—
The amateur is very rare in French literature-as rare as he is common in our own. (G. L. Strachey.)
ইংরেজি সাহিত্যের এই amateurishness আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যেমন-তেমন করে যা-হোক-একটা-কিছু লিখে ফেলার ভিতর কোনোরূপ আয়াস নেই, কোনোরূপ আত্মসংযম নেই।
ফরাসি সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুইই লেখকদের সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়। কেননা সংযম ব্যতীত, কি মনোজগতে, কি কর্মজগতে, কোনো বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ করা যায় না। সংস্কৃতে একটি কথা আছে যে ‘যোগঃ কর্মসু কৌশলং’। রচনা সম্বন্ধে এই কৌশল লাভ করতে হলে লেখকদের পক্ষে যোগ অভ্যাস করা দরকার। অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে কোথাও বা হঠযোগ, কোথাও বা রাজযোগ। বাহুল্য আর ঐশ্বর্য, স্ফীতি আর শক্তি যে এক বস্তু নয়, এ সত্য ফরাসি সাহিত্য মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।
তার পর সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়েও উক্ত সাহিত্য আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়। আমি পূর্বে বলেছি যে, ভাষা সাহিত্যের উপাদান, কিন্তু এ কথা শুধু আংশিক ভাবে সত্য। আসল সত্য এই যে, লেখকদের নিকট ভাষা একাধারে উপাদান ও যন্ত্র। আমাদের দেশে সর্ব শ্রেণীর শিল্পীরা বৎসরে অন্তত একবার যন্ত্রপূজা করে থাকে, একমাত্র একালের সাহিত্য-শিল্পীরাই তাঁদের যন্ত্রকে পূজা করা দূরে থাক্, মেজে-ঘষে পরিষ্কারও করেন না। ফরাসি সাহিত্য আমাদের এই যন্ত্রকে লঘু করতে, তীক্ষ্ণ করতে শেখায়। এ শিক্ষা আমরা সহজেই আত্মসাৎ করতে পারি, কেননা আমার বিশ্বাস, বাংলার সঙ্গে ফরাসি ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের ভাষাও মূলতঃ এক, এবং বিদেশি শব্দে তা ভারাক্রান্ত নয়। আমাদের ভাষার অন্তরেও ফরাসি ভাষার গতি ও স্ফুর্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্যগ্রন্থ জর্মানের ন্যায় স্থূলকায় গুরুভার শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসি সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস বলে গণ্য হত।
আমরা যে-ভাষায় এখন সাহিত্য রচনা করি, সে ভারতচন্দ্রের ভাষা নয়; ইতিমধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে আমরা সে-ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছি, অর্থাৎ তার গায়ে একরাশ মুখস্থকরা শব্দ চাপিয়ে দিয়ে তার ভার বৃদ্ধি করেছি, তার গতি মন্দ করেছি। ফরাসি সাহিত্যের শিক্ষা আমাদের মনে বসে গেলে আমরা আবার বহুসংখ্যক পণ্ডিতি শব্দকে সসম্মানে বিদায় করব এবং তার পরিবর্তে বহুসংখ্যক তথাকথিত ইতর শব্দকে সাহিত্যে বরণ করে নেব। কেননা এই কৃত্রিম ভাষার চাপে আমাদের জাতীয় প্রতিভা মাথা তুলতে পারছে না।
১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ
বই পড়া
কটেজ লাইব্রেরি ও ভবানীপুর ইনস্টিটিউটের সাহিত্যশাখার অধিবেশনে পঠিত
প্রবন্ধ আমি লিখি এবং সম্ভবতঃ যত লেখা উচিত তার চাইতে বেশিই লিখি, কিন্তু সে প্রবন্ধ সর্বজনসমক্ষে পাঠ করতে আমি স্বভাবতই সংকুচিত হই। লোকে বলে, আমার প্রবন্ধ কেউ পড়ে না। যে প্রবন্ধ লোকে স্বেচ্ছায় পড়ে না, সে প্রবন্ধ অপরকে পড়ে শোনানোটা অবশ্য শ্রোতাদের উপর অত্যাচার করারই শামিল।
এ সত্ত্বেও আমি আপনাদের অনুরোধে আজ যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে প্রস্তুত হয়েছি তার কারণ, লাইব্রেরি সম্বন্ধে কথা কইবার আমার কিঞ্চিং অধিকার আছে।
কিছুদিন পূর্বে সাহিত্য পত্রে আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, আমি একজন ‘উদাসীন গ্রন্থকীট’। এর অর্থ, কোনা-কোনো ােেক যেমন সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বনে গমন করেন, আমিও তেমনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছি। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে আমি যে আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি, এ জ্ঞান আমার অবশ্য ইতিপূর্বে ছিল না। সে যাই হোক, আমার আকৈশোর বন্ধু শ্ৰীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দত্ত এই সার্টিফিকেটের বলে এ ক্ষেত্রে বই পড়া সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে সাহসী হয়েছি। লাইব্রেরিতে বইয়ের গুণগান করাটা, আমার বিশ্বাস, অসংগত হবে না।
২.
আজকের সভায়, যে দু-চার কথা বলব, সে আলাপের ভাষায় ও আলাপের ভাবে, অর্থাৎ তাতে কাজের কথার চাইতে বাজে কথা ঢের বেশি থাকবে। এই বিংশ শতাব্দীতে লাইব্রেরির সার্থকতা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কথা বলবার কি প্রয়োজন আছে? এ সম্বন্ধে যা বক্তব্য তা ইতিপূর্বে হাজার বার কি বলা হয় নি। তবে বই পড়ার অভ্যাসটা যে বদ অভ্যাস নয়, এ কথাটা সমাজকে এ যুগে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। কেননা মানুষে এ কালে বই পড়ে না, পড়ে সংবাদপত্র। এ যুগে সভ্য সমাজ ভোরে উঠে করে দুটি কাজ : এক চা-পান, আর সংবাদপত্রপাঠ। একটি বিলাতি কবি চায়ের সম্বন্ধে বলেছেন যে, The cup that cheers but not inebriates, অর্থাৎ, চা পান করলে নেশা হয় না অথচ ফুর্তি হয়। চা পান করলে নেশা না থোক, চা-পানের নেশা হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধে ঐ একই কথা খাটে। তার পর অতিরিক্ত চা-পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়, অতিরিক্ত সংবাদপত্রপাঠের ফলেও মানুষের তেমনি সাহিত্যে অরুচি হয়। আমরা দেশসুদ্ধ লোক আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং সাহিত্যচর্চা করবার প্রথাটা যে সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ, এই সত্যটার চার দিকে আজ প্রদক্ষিণ করবার সংকল্প করেছি।
৩.
কাব্যচর্চা না করলে মানুষে জীবনের একটা বড় আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায়। বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে।) সুতরাং কোনো সভ্যজাতি কস্মিকালে তার দিকে পিঠ ফেরায় নি; এ দেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য, এমন কথা বললে বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রা-কলহে দিনযাপন করার চাইতে কাব্যচর্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলেই সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃতাপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে সে উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করতেন কি না, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। কিছুদিন পূর্বে আমারও ছিল। কেননা নিজের কলমের কালি লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও আমরা যখন ওসব কথায় ভুলি নে, তখন সেকালেও সম্ভবতঃ কেউ ভুলতেন না; কেননা সেকালে সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশি ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই পড়াটা নাগরিকদের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফ্যাশন ছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ‘নাগরিক’ বলতে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাত একালে ইংরেজিতে যাকে inan about town বলে। বাংলা ভাষায় ওর কোনো নাম নেই,; কেননা বাংলাদেশে ও-জাত নেই। ও বালাই যে নেই, সেটা অবশ্য সুখের। বিষয়।
৪.
যদি অনুমতি করেন তো এই সুযোগে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। সেকালে এ দেশে যেমন একদল ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, তেমনি আর-এক দল ভোগী পুরুষও ছিলেন। ভারতবর্ষের আরণ্যক ধর্মের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু তার নাগরিক ধর্মের ক্রিয়াকলাপ আমাদের অনেকের কাছেই অবিদিত। এর ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ধারণাটা আমাদের মনে নিতান্ত একপেশে হয়ে উঠেছে। সে সভ্যতার, শুধু আত্মার নয়, দেহের সন্ধানটাও আমাদের নেওয়া কর্তব্য, নচেৎ তার স্বরূপের সাক্ষাৎ আমরা পাব না। সেকালের নাগরিকদের মতিগতি রীতিনীতির আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায় কামসূত্রে। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর পূর্বে, এবং এ গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন ন্যায়দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বয়ং বাৎস্যায়ন; অতএব কামসূত্রের বর্ণনা আমরা সত্য বলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য, বিশেষতঃ ও-সূত্র যখন সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্র হিসেবেই চিরকাল গণ্য ও মান্য হয়ে এসেছে। আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার আংশিক বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি–
বাহিরে বাসগৃহেও অতিশুভ্রচাদরপাতা শষ্যা একটি থাকিবে, এবং তাঁহার উপর দুইটি অতি সুন্দর বালিশ রাখিতে হইবে। তাঁহার পার্শ্বে থাকিবে প্রতিশয্যিকা। এবং তাঁহার শিরোভাগে কূচস্থান ও বেদিকা স্থাপিত করিবে। সেই বেদিকার উপর রাত্রিশেষে অনুলেপন, মাল্য, শিক্থকরণ্ডক, সৌগন্ধিকপূটিকা, মাতুলুঙ্গত্বক, তাম্বুল প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। ভূমিতে থাকিবে পতংগ্রহ। ভিত্তিগাত্রে নাগদন্তাবসক্তা বীণা। চিত্রফলক। বতিক-সমুদগকঃ এবং যে কোনো পুস্তক।
উপরোক্ত বর্ণনা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। কেননা এর অনেক শব্দই বাংলা ভাষায় প্রচলিত নেই। আমি কতকটা টীকা ও কতকটা অভিধানের সাহায্যে এসকল অপরিচিত শব্দের বাচ্যপদার্থের যে পরিচয় লাভ করেছি, তা আপনাদের জানাচ্ছি। প্রতিশয্যিকার অর্থ ক্ষুদ্র পর্যঙ্ক, ভাষায় যাকে বলে খাঁটিয়া; এ খাঁটিয়া অবশ্য নাগরিকরা নিজেদের গঙ্গাযাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখতেন না। তার মাথার গোঁড়ায় থাকত কূর্চস্থান; কূর্চ শব্দের সাক্ষাৎ আমি কোনো অভিধানে পাই নি। তবে টীকাকার বলেন, শয্যার শিরোভাগে ইষ্টদেবতার আসনের নাম কূর্চ; আত্মবান নাগরিকেরা ইষ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণাম না করে শয়নগ্রহণ করতেন না সুতরাং কূর্চ হচ্ছে এক প্রকার ব্রাকেট। সেকালের এই বিলাসীসম্প্রদায়, আমরা যাকে বলি নীতি, তার ধার এক কড়াও ধারতেন না; কিন্তু দেবতার ধার ষোলো আনা ধারতেন। এ ব্যাপার অবশ্য অপূর্ব নয়। একালেও দেখা যায় মানুষের প্রতি অত্যহিত অত্যাচার করবার সময় মানুষে ইষ্টদেবতাকে ঘন ঘন স্মরণ ও প্রণাম করে। যাক ওসব কথা। এখন দেখা যাক, বেদিকা বস্তুটি কি। বেদিকাতে যত প্রকার দ্রব্য রাখবার ব্যবস্থা আছে, তাতে মনে হয় ও হচ্ছে টেবিল; এবং টীকাকারের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ অনুমান ভুল নয়; তিনি বলেন, বেদিকা ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ এবং কৃতকুট্টিম অর্থাৎ inlaid। অনুলেপন দ্রব্যটি হয় চন্দন, নয় মেয়েরা যাকে বলে রূপটান, তাই। মাল্য অবশ্য ফুলের মালা; কি ফুল তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আর যাই হোক গাদা নয়; কেননা তারা বর্ণগন্ধের সৌকুমার্য বুঝতেন। সিথকরণ্ডক হচ্ছে মোমের কৌটা; সেকালে নাগরিকেরা ঠোঁট আগে মোম দিয়ে পালিশ করে নিয়ে তার পর তাতে আলতা মাখতেন। সৌগন্ধিকপূটিকা হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে পাউডার-বক্স; বোতল না হয়ে বাক্স হবার কারণ, সেকালে অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য চূর্ণ আকারেই ব্যবহৃত হত। দেয়াল ছেড়ে ঘরের মেজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই চোখে পড়ে পতৎগ্রহ, অর্থাৎ পিকদানি। তার পর চোখ তুললে নজরে পড়ে, ভিত্তিসংলগ্ন হস্তিদন্তে বিলম্বিত বীণা; টীকাকার বলেন, সে বীণা আবার ‘নিচোলঅবগুণ্ঠিতা; বাংলার অনেক পদ্যলেখকদের ধারণা নিচোল অর্থে শাড়ি, শাড়িপরা বীণার অবশ্য কোনো মানে নেই; নিচোল অর্থে গেলাপ; জয়দেব যে শ্রীরাধিকাকে বলেছিলেন ‘শীলয় নীল নিচোলং’, তার অর্থ নীল রঙের একটি ঘেরাটোপ পরো; ইংরেজি ভাষায় ওর তর্জমা হচ্ছে, put on a dark-blue cloak। এখন আবার প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক। তার পর পাই চিত্রফলক; সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, পুরাকালে ছবি কাঠের উপরে আঁকা হত, কাপড়ের উপরে নয়। বর্তিকা সমুকের অর্থ তুলি ও রং রাখবার বাক্স। তার পর বই।
নাগরিকদের গৃহের এবং দেহের এই সাজসজ্জার বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারবেন তারা কি চরিত্রের লোক ছিলেন। তার পর প্রশ্ন ওঠে, বই নিয়ে এ প্রকৃতির লোকেরা কি করতেন? কেননা নাগরিকেরা আর যাই হোন, তারা যে সব উদাসীন গ্রন্থকীট ছিলেন না, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। পুস্তক কি তবে এঁদের গৃহসজ্জার জন্য রক্ষিত হত, যেমন আজকাল কোনো কোনো ধনীলোকের গৃহে হয়? এ সন্দেহ দৃঢ় হয়ে আসে, যখন টীকাকারের মুখে শুনতে পাই যে,
এইসকল বীণাদিদ্রব্য সর্বদা উপঘাতের, অর্থাৎ ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিবার জন্য, নহে। কেবল বাসগৃহের শোভা সম্পাদনার্থ ভিত্তিনিহিত হস্তিদন্তে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কালে ভদ্রে কখনো প্রয়োজন হইলে তাহা সেখান হইতে নামাইতে হইবে।
পূর্বোক্ত সন্দেহের অরিও কারণ আছে। সূত্রকার যখন বলেছেন— ‘যঃ কশ্চিং পুস্তকং’, অর্থাৎ যা হোক একটা বই, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে-বই, আর যে কারণেই হোক, পড়বার জন্য রাখা হত না। কিন্তু টীকাকার আমাদের এ সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। তাঁর কথা এই–
‘য কশ্চিৎ’ এটি সামান্য নির্দেশ হইলেও তখনকার যে-কোনো কাব্য তাহাই পড়িবার জন্য রাখিবে, ইহাই যে সূত্রকারের উপদেশ, তা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।
টীকাকারের এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রাহ্য করি। বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও ও-দুই গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না। বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য, পুস্তকপঠন অপেক্ষাকৃত ঢের সহজ। সুতরাং বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীণা বাজাবার অধিকার তার সিকির সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে, কিন্তু কাউকে জোর করে সংগীতশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোনো অসভ্য দেশেও নেই। অতএব নাগরিকেরা বীণা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন বলে যে পুঁথির ডুরি খুলতেন না, এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে। সে যাই হোক, টীকাকার বলেছেন, “যে-সে বই নয়, তখনকার বই; এই উক্তিই প্রমাণ যে, সে বই পড়া হত। যে বই এখনকার নয় কিন্তু সেকালের, যাকে ইংরেজিতে বলে ক্ল্যাসিক, তা ভদ্রসমাজে অনেক লোক ঘরে রাখে পড়বার জন্য নয়, দেখবার জন্য। কিন্তু হালের বই লোকে পড়বার জন্যই সংগ্রহ করে, কেননা অপর কোনো উদ্দেশ্যে তা গৃহজাত করবার কোনোরূপ সামাজিক দায় নেই। আর-এক কথা। আমরা বর্তমান ইউরোপের সভ্যসমাজেও দেখতে পাই যে, এখনকার’ বই পড়া সে সমাজের সভ্যদের ) ফ্যাশনের একটি প্রধান অঙ্গ। আনাতোল ফ্রাসের টাটকা বই পড়ি নি, এ কথা বলতে প্যারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হবেন, সম্ভবতঃ কিপলিঙের কোনো সদ্যপ্রসূত বই পড়ি নি বলতে লণ্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন; যদিচ আনতোল ফ্রাঁসের লেখা যেমন সুপাঠ্য, কিপলিঙের লেখা তেমনি অপাঠ্য। এ কথা আমি আন্দাজে বলছি নে। বিলেতে একটি ব্যারিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। জনরব, তিনি মাসে দশ-বিশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। অত না হোক, যা রটে তা কিছু বটেই তো। এই থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারেন, তিনি ছিলেন কত বড় লোক। এত বড় লোক হয়েও তিনি একদিন আমার কাছে, অস্কার ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি, এই কথাটা স্বীকার করতে এতটা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন, যতটা চোর-ডাকাতরাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে guilty plead করতে সচরাচর করে না। অথচ তার অপরাধটা কি? অস্কার ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি, এই তো? ওসব বই পড়েছি স্বীকার করতে আমরা লজ্জিত হই। শেষটা তিনি এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ত দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন যে, আইনের অশেষ নজির উদরস্থ করতেই তাঁর দিন কেটে গিয়েছে, সাহিত্য পড়বার তিনি অবসর পান নি। বলা বাহুল্য, এ রকম ব্যক্তিকে এ দেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, এ কথা কবুল করতে তিনি যে এতটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণ, তার এ জ্ঞান ছিল যে, তিনি যত আইনজ্ঞই হোন, আর যত টাকাই করুন, তার দেশে ভদ্রসমাজে কেউ তাকে বিদগ্ধজন বলে মান্য করবে না।
সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এ দেশে পুরাকালে কাচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আমরা যাকে সত্য বলি সেকালে তাকে নাগরিক বলত। অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্যায়-শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে synonyms.
৫.
এর উত্তরে হয়ত অনেকে এই কথা বলবেন যে, সেকালে বই পড়াটা ছিল। বিলাসের একটা অঙ্গ। বাৎস্যায়নই যখন আমার প্রধান সাক্ষী, তখন এ অভিযোগের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে কঠিন। এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করি নে, ও চর্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফললাভের প্রত্যাশা রাখি। আপনারা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে মাল্য-চন্দন-বনিতা এ-তিন একসঙ্গেই যায়, এবং ও-তিনই ছিল এক পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আমাদের কাছে মাল্যচন্দনের শামিল বনিতাও নয়, কবিতাও নয়। কাজেই আমাদের চোখে সেকালের নাগরিকসমাজের রীতিনীতি অবশ্য দৃষ্টিকটু ঠেকে। কেননা আমাদের চোখের পিছনে আছে আমাদের মন, এবং আমাদের মনের পিছনে আছে আমাদের বর্তমান সামাজিক বুদ্ধি। এই কারণেই প্রাচীন সমাজের প্রতি সুবিচার করতে হলে সে সমাজকে ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে দেখা কর্তব্য। তাই আমি উদাসীন গ্রন্থকীট হিসেবে নাগরিকদের উক্তরূপ সাহিত্যচর্চার ফলাফল একটুখানি আলোচনা করে দেখতে চাই। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক হতে হলে প্রথমতঃ বর্তমানের প্রতি উদাসীন হওয়া চাই, দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন গ্রন্থের কীট হওয়া চাই; আরও অনেক হওয়া চাই, কিন্তু ও-দুটি না হলে নয়।
যে সমাজে কাব্যচর্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য, এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ অর্থে তারা বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে, এবং তা ছাড়া আর-কিছু করে না। অপর পক্ষে যে সমাজের আয়েসির দলও কাব্যকলার আদর করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিডি ভেঙেছে। সভ্যতা জিনিসটে কি, এ। প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা মূর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং কোনো সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয়; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতিত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানেবিজ্ঞানে কাব্যকলায় শিল্পে-বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ব্যবধান। জনৈক ফরাসি লেখক বলেছেন যে, যিনিই মানবের ইতিহাস চর্চা করেছেন, তিনিই জানেন যে, মানুষকে ভালো করবার চেষ্টা বৃথা। এ হচ্ছে অবশ্য ক্ষুব্ধ মনের ক্রুদ্ধ কথা, অতএব বেদবাক্য হিসেবে। গ্রাহ্য নয়। সে যাই হোক, এ কথার উত্তরে আমি বলি যে, মানুষকে ভালো করা যাক, ভদ্র করা যায়। পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান্ না করলেও রুচিমান করত। সমাজের পক্ষে এও একটা কম লাভ নয়।
ধরে নেওয়া যাক, সেকালের নাগরিকসমাজ কাব্যকে মনের বেশভূষার উপকরণ হিসেবে দেখত। তারা যে হিসাবে ওষ্ঠে যুবক ধারণ করতেন, সেই হিসাবেই কণ্ঠে শ্লোক ধারণ করতেন। এ অনুমান নিতান্ত অমূলক নয়। সংস্কৃত ভাষায় একটি নাতিহ্রস্ব শ্লোকসংগ্রহ আছে, যার নাম বিদগ্ধমুখমণ্ডন। ও রকম নামকরণের ফলে কাব্য অবশ্য রঙের কোঠায় পড়ে যায়। সে যাই হোক, নাগরিকদের বই পড়া যে একেবারে ভস্মে ঘি ঢালার শামিল ছিল না, এবং তাদের বৈদগ্ধ্য যে তাদের মনুষ্যত্ব অনেকটা রক্ষা করেছিল, একটি উদাহরণের সাহায্যে তার প্রমাণ দিচ্ছি। চরিত্রহীন অথচ কলাকুশল নাগরিকদের সেকালে সাধারণ সংজ্ঞা ছিল ‘বিট। এই বিটের একটি ছবি আমরা মৃচ্ছকটিকে দেখতে পাই। ঐ নাটকের রাজশ্যালক শকারের সঙ্গে বিটের তুলনা করলেই নিরক্ষর ও বিদগ্ধ জনের প্রকৃতির তারতম্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। উভয়েই সমান বিলাসভক্ত, কিন্তু শকার পশু আর বিট সুজন। শকারের ব্যবহার দেখলে ও কথা শুনলে তাকে অর্ধচন্দ্র দিতে হাত নিশপিশ করে; অপর পক্ষে বিটের ব্যবহারের সৌজন্য, ভাষার আভিজাত্য, মনের সরসতা এত বেশি যে, তাকে সাদরসম্ভাষণ করে ঘরে এনে বসাতে ইচ্ছে যায় দু দণ্ড আলাপ করবার জন্য। বৈদগ্ধ্য যে একটি সামাজিক গুণ, এ কথা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হবে। মার্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবতঃ চিরকাল করবে। এসকল বস্তু সমাজকে উন্নত না হোক, অলংকৃত করে। এবং এসকল গুণ কাব্য ও কলার চর্চা ব্যতীত রক্তমাংসের শরীরে আপনা হতে ফুটে ওঠে না। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সভ্যতা এসকল গুণের যতটা মূল্য দিত, আমরা ততটা দিই নে। তার কারণ, সেকালের সভ্যতা ছিল অ্যারিস্টোক্রাটিক, আর একালের সভ্যতা হতে চাচ্ছে ডেমোক্রাটিক; সেকালে তাঁরা চাইতেন আকার, আমরা চাই বস্তু। তারা দেখতেন মানুষের ব্যবহার, আমরা দেখতে চাই তার ভিতরটা। তাঁরা ছিলেন রূপভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ। ক্ল্যাসিক সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তুলনা করলে এ প্রভেদ সকলেরই চোখে ধরা পড়বে। এ যুগের সাহিত্যমাত্রেই রোমান্টিক, অর্থাৎ তাতে আর্টের ভাগ কম এবং আত্মার ভাগ বেশি। এর কিরণ, এ যুগের কবিরা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন; এ যুগের কবি জনগণের প্রতিনিধিও নন, মুখপাত্রও নন; সুতরাং সে কবির মন নিজের মন, লৌকিক মনও নয় সামাজিক মনও নয়। আর সেকালের কবিরা সামাজিকদের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করতেন। সেকালের সামাজিকেরা কলাবিং ছিলেন বলে সেকালের কবিরা রচনায় বস্তুর অপেক্ষা তার আকারের দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে বাধ্য হতেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে দেখতে পাই, কবি কি বললেন, তার চাইতে কি ভাবে বললেন তার মর্যাদা ঢের বেশি। সুতরাং নাগরিকদের কাব্যচর্চার ফলে প্রাচীন সাহিত্য যে আর্টিস্টিক হয়েছে, এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। এইসব কারণে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, নাগরিকদের কাব্যচর্চা একেবারে নিষ্ফল হয় নি, কেননা তার গুণে ক্ল্যাসিক সাহিত্য অসামান্য সুষমা ও সামঞ্জস্য লাভ করেছে।
কাব্যে অর্টের মূল্য যে কত বড়, সে আলোচনায় অজি প্রবৃত্ত হব না, কেননা সে আলোচনা দু কথায় শেষ করবার জো নেই। বহু যুক্তি বহু তর্কের সাহায্যে ও-সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আমি পূর্বেই বলেছি, এ যুগের ডেমোক্রাটিক আত্মা আর্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, সম্ভবতঃ মনে। মনে হিংসাও করে; বোধ হয় এই কারণে যে, আর্টের গায়ে আভিজাত্যের ছাপ চিরস্থায়ী রূপে বিরাজ করে। অথচ ডেমোক্রাসির এ-সত্য সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, লৌকিক মন বস্তুগত বলেই তা মেটিরিয়ালিজুমের দিকে সহজেই ঝোঁকে। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর্টের চর্চা আবশ্যক।
৬
বই পড়ার শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমতঃ সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই; দ্বিতীয়তঃ অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেননা আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগশোক-দুঃখদারিদ্র্যের দেশে জীবনধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবতঃ নির্মমও ‘ ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আজ প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলেই উহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবতঃ দুরাশা; কিন্তু তাহলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে, কেননা আমাদের উদ্ধারের অন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাই নে। শিক্ষার মাহাত্মে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যা বলুন, সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে। কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার-দর নেই। এই কারণেই ডেমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমোক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে, কিন্তু তাদের শিষ্যেরা তাদের কথা উলটো বুঝে প্রতিজনেই হতে চায় বড়মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্র্যাসির গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিতসমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে, সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান। যারা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তারা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন; কেননা তাতে ব্যাবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে, সে তো জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো। প্রত্যক্ষ; কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ঊড়েও ভবানী। তার পর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন, জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ এবং মানুষের মনকে সবল, সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত। হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান ধর্ম-নীতি অনুরাগ-বিরাগ আশানৈরাশ্য তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য, এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সেসব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান, ইত্যাদি সব হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।
অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তেই হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নৈই। ধর্মের চর্চা চাইকি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে, এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। ও চর্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না, চিড়িয়াখানাতেও নয়।।
এসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, লাইব্রেরির মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।
আমার মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুলকলেজের চাইতে কিছু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসে উঠবেন। কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছি নে, অদ্ভুত কথাও বলছি নে; যদিচ এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্যমিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে, তাহলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।
আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই, এমনকি এ ক্ষেত্রে দাতা কর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তারা বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞানপিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর-কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত-বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।
আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন, যারা শিশুসন্তানকে ক্রমান্বয়ে গোরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ডোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে, এ জ্ঞান ও-শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাদের বিশ্বাস, ও বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে, তাহলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে-বেঁধে জোরজবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটা সে যখন এই দুগ্ধপানক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য মাথা নাড়তে, হাতপা ছুড়তে শুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখো, এই ঢোক, আর-এক ঢোক, আর-এক ঢোক ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা-কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান, এবং ঢোকের পর ঢেকে তার মরা মুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুলকলেজের শিক্ষাপদ্ধতিটাও ঐ একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে ইফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে, তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।
৭.
আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি, দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে; পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষাশাস্ত্রের একজন জগদবিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময় ফরাসিদেশে শিক্ষাপদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে-যুগে France was saved by her idlers : অর্থাৎ যারা পাস করতে পারে নি কিংবা চায় নি, তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।
সে যুগে ফ্রান্সে কি রকম শিক্ষা দেওয়া হত তা আমার জানা নেই, তবুও আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুলকলেজে শিক্ষার যে রীতি চলছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কখনোই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাস্টারমহাশয়েরা নোট দেন এবং সেই নোট মুখস্থ করে ছেলেরা হয় পাস। এর জুড়ি আর-একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এ দেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গোলা পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তার পর একে একে সবগুলি উগলে দেয়। এর ভিতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগলানো দর্শকের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্তপরিচ্ছেদ ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারা ঐ লোহার গোলাগুলির এক কণাও জীর্ণ করতে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলাগুলি বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্গিরণ করে দেয়। এর জন্য সমাজ তাদের বাহবা দেয় দিক, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এতে জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। স্কুলকলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ, সে বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি, শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক; কেননা আমাদের স্কুলকলেজ ছেলেদের স্বশিক্ষিত হবার যে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট। করে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে, তার আপনার বলতে আর বেশি কিছু থাকে না, যদি-না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ক্ষীণ প্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষাপদ্ধতিও যাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারে না।
আমি লাইব্রেরিকে স্কুলকলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুলকলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।
৮.
অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষতঃ প্রাচীন নজির দেখাবার, কি প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভালো, তা কে না মানে? আমার উত্তর, সকলে মুখে মানলেও, কাজে মানে না। মুসলমানধর্মে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত : এক যারা কেতাবি, আর-এক যারা তা নয়। বাংলার শিক্ষিতসমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয় এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না; আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুইই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়, কেননা সাহিত্য সাক্ষাভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই, অথচ এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু এ কথা আমরা সকলে মানি নে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্তব্য, কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে, মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায়, ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ তিলাভ করে না। তার পর যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা, অতএব কোনো নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না, অর্থনীতির নয় ধর্মনীতিরও নয়।
কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে, সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব, এ কথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও যে আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উলটো টান যে আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার সপক্ষে এত বাক্যব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কি না জানি নে; সম্ভবতঃ হই নি। কেননা আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালিকোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই, কড়ি লাগাতে হয়।
আপনাদের কাছে আমার আর একটি নিবেদন আছে। এ প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের নাগরিক সভ্যতার উল্লেখটা, কতকটা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। এ কাজ আমি বিদ্যে দেখাবার জন্য করি নি, পুঁথি বাড়াবার জন্যও করি নি। এই ডেমোক্রাটিক যুগে অ্যারিস্টোক্রাটিক সভ্যতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। আমার মতে এ যুগের বাঙালির আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে এথেন্স যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান অধিকার করবে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, তা ছিল একাধারে ডেমোক্রাটিক এবং অ্যারিস্টোক্রাটিক; অর্থাৎ সে সভ্যতা ছিল সামাজিক জীবনে ডেমোক্রাটিক এবং মানসিক জীবনে অ্যারিস্টোক্রাটিক। সেই কারণেই গ্রীক সাহিত্য এত অপূর্ব, এত অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোনো বিচ্ছেদ নেই; বরং দুয়ের মিলন এত ঘনিষ্ঠ যে, বুদ্ধিবলে তা বিশ্লিষ্ট করা কঠিন। আমাদের কর্মীর দল যেমন এক দিকে বাংলায় ডেমোক্রাসি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি আর-এক দিকে আমাদেরও পক্ষে মনের অ্যারিস্টোক্রাসি গড়ে তোলবার চেষ্টা করা কর্তব্য। এর জন্য চাই সকলের পক্ষে কাব্যকলার চর্চা। গুণী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মনের মিলন না হলে কাব্যকলার আভিজাত্য রক্ষা করা অসম্ভব। সাহিত্যচর্চা করে দেশসুদ্ধ লোক গুণজ্ঞ হয়ে উঠুক, এই হচ্ছে। দেশের লোকের কাছে আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা।
১৩২৫ শ্রাবণ
বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ
নানারূপ গদ্যপদ্য লেখবার এবং ছাপবার যতটা প্রবল ঝোঁক যত বেশি লোকের মধ্যে আজকাল এদেশে দেখা যায়, তা পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। এমন মাস যায় না, যাতে অন্তত একখানি মাসিকপত্রের না আবির্ভাব হয়। এবং সেসকল মাসিকপত্রে সাহিত্যের সকলরকম মালমশলার কিছু-না-কিছু, নমুনা থাকেই থাকে। সুতরাং একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বঙ্গসাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এই নবযুগের শিশু-সাহিত্য আঁতুড়েই মরবে কিংবা তার এক শ বৎসর পরমায়ু হবে, সেকথা বলতে আমি অপারগ। আমার এমন কোনো বিদ্যে নেই, যার জোরে আমি পরের কুষ্টি কাটতে পারি। আমরা সমুদ্রপার হতে যেসকল বিদ্যার আমদানি করেছি, সামুদ্রিক বিদ্যা তার ভিতর পড়ে না। কিন্তু এই নবসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলির বিষয় যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মায়, তাহলে যুগধর্মানুযায়ী সাহিত্যরচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। পূর্বোক্ত কারণে নব্যলেখকরা তাঁদের লেখায় যে হাত দেখাচ্ছেন, সেই হাত দেখবার চেষ্টা করাটা একেবারে নিষ্ফল নাও হতে পারে।
প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এদেশের সাহিত্যজগৎ যখন দু-চার জন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দুরে থাক পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন; এবং তাঁরা কাব্য দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে মন্দির অট্টালিকা স্তুপ স্তম্ভ গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনোরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে তোলা অসম্ভব, এই জ্ঞানটুকু জন্মালে আমাদের কারও আর সাহিত্যে রাজা হবার লোভ থাকবে না এবং শব্দের কীর্তিস্তম্ভ গড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত করব না। এর জন্য আমাদের কোনোরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই। বস্তুজগতের ন্যায় সাহিত্যজগতেরও প্রাচীন কীর্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভালো, কিন্তু নিত্যব্যবহার্য নয়।
দর্শনের কুতবমিনারে চড়লে আমাদের মাথা ঘোরে; কাব্যের তাজমহলে রাত্রিবাস করে চলে না, কেননা অত সৌন্দর্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন। ধর্মের পর্বতগুহার অভ্যন্তরে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো যায় না, আর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালেই যে কোনো অমুল্য চিন্তামণি আমাদের হাতে ঠেকতে বাধ্য, এ বিশ্বাসও আমাদের চলে গেছে। পুরাকালে মানুষে যা-কিছু, গড়ে গেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হতে আলগা করা, দু-চারজনকে বহলোক হতে বিচ্ছিন্ন করা। অপরপক্ষে নবযুগের ধর্ম হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা, কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বহৎ না হলে যে কোনো জিনিস মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্তি গলি আকারে ছোট হয়ে আসবে, কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে; আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাব্যদর্শনাদি আর গাছের মত উচুর দিকে ঠেলে উঠবে না, ঘাসের মত চারিদিকে চারিয়ে যাবে। এককথায় বহশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নবসয উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্তত ষষ্টি সহস্র বালখিল্য-লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। এরূপ হবার কারণও সুস্পষ্ট। আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাকলেও লেখবার যথেষ্ট সময় নেই, লেখবার অবসর থাকলেও লিখতে শেখবার অবসর নেই; অথচ আমাদের লিখতেই হবে, নচেৎ মাসিকপত্র চলে না। এ যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিকপত্রের পঠপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়; কেননা, মাসিকপত্রের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পয়লা বেরনো; কি যে বেরলো, তাতে বেশি-কিছু আসে-যায় না। তাছাড়া, আমাদের সকলকেই সকল বিষয়ে লিখতে হয়। নীতির জতোশেলাই থেকে ধর্মের চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সকল ব্যাপারই আমাদের সমান অধিকারভুক্ত। আমাদের নবসাহিত্যে কোনোরূপ ‘শ্রমবিভাগ’ নেই, তার কারণ যে-ক্ষেত্রে ‘শ্রম’-নামক মূল পদার্থেরই অভাব সেস্থলে তার বিভাগ আর কি করে হতে পারে।
তাই আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোটগল্প খণ্ডকাব্য সরলবিজ্ঞান ও তরলদর্শন।
দেশকালপাত্রের সমবায়ে সাহিত্য যে ক্ষদ্রধর্মাবলম্বী হয়ে উঠেছে, তার জন্য আমার কোনো খেদ নেই। একালের রচনা ক্ষদ্র বলে আমি দুঃখ করি নে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয়, তাহলে সে জিনিসের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই। লেখকরা এই সত্যটি মনে রাখলে গল্প স্বল্প হয়ে আসবে, শোক লোকরপ ধারণ করবে, বিজ্ঞান বামনরপ ধারণ করেও ত্রিলোক অধিকার করে থাকবে এবং দর্শন নখদর্পণে পরিণত হবে। যাঁরা মানসিক আরামের চর্চা না করে ব্যায়ামের চর্চা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, যে সাহিত্যে দম নেই, তাতে অন্তত কস (grip) থাকা আবশ্যক।
২.
বর্তমান ইউরোপের সম্যক পরিচয়ে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে, গণধর্মের প্রধান ঝোঁক হচ্ছে বৈশ্যধর্মের দিকে; এবং সেই ঝোঁকটি না সামলাতে পারলে সাহিত্যের পরিণাম অতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমাদের এই আত্মসর্বস্ব দেশে লেখকেরা যে বৈশ্যবত্তি অবলম্বন করবেন না, একথাও জোর করে বলা চলে না। লক্ষ্মীলাভের আশায় সরস্বতীর কপট সেবা করতে অনেকে প্রস্তুত, তার প্রমাণ ‘ভ্যালু-পেয়বল্ পোস্ট’ নিত্য ঘরে ঘরে দিচ্ছে। আমাদের নবসাহিত্যের যেন-তেন-প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবত্তিটি যদি দমন করতে না পারা যায়, তাহলে বঙ্গসরস্বতীকে যে পথে দাঁড়াতে হবে, সেবিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কোনো শাস্ত্রেই একথা বলে না যে, বাণিজ্যে বসতে সরস্বতী। সাহিত্যসমাজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার ইচ্ছে থাকলে দারিদ্র্যকে ভয় পেলে সে আশা সফল হবে না। সাহিত্যের বাজার-দর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে, সেইসঙ্গে তার মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের লোপ পেয়ে আসবে। সুতরাং আমাদের নবসাহিত্যে লোভ-নামক রিপর অস্তিত্বের লক্ষণ আছে কি না, সেবিষয়ে আমাদের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক; কেননা, শাস্ত্রে বলে, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।
৩.
এ যুগের মাসিকপত্রসকল যে সচিত্র হয়ে উঠেছে সেটি যেমন আনন্দের কথা, তেমনি আশঙ্কারও কথা। ছবির প্রতি গণসমাজের যে একটি নাড়ির টান আছে, তার প্রচলিত প্রমাণ হচ্ছে মার্কিন সিগারেট। ঐ চিত্রের সাহচর্যেই যত অচল সিগারেট বাজারে চলে যাচ্ছে। এবং আমরা চিত্রমন্ধ হয়ে মহানন্দে তাম্রকটজ্ঞানে খড়ের ধম পান করছি। ছবি ফাউ দিয়ে মেকি মাল বাজারে কাটিয়ে দেওয়াটা আধুনিক ব্যাবসার একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীতেই চিত্রের প্রথম আবির্ভাব। পুস্তিকায় এবং পত্রিকায় ছেলেভুলোনো ছবির বহুল প্রচারে চিত্রকলার যে কোনো উন্নতি হবে, সেবিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে; কেননা, সমাজে গোলাম পাশ করে দেওয়াতেই বণিকবুদ্ধির সার্থকতা, কিন্তু সাহিত্যের যে অবনতি হবে, সেবিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। নতকীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ সারঙ্গীর মত চিত্রকলার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ কাব্যকলার অনুধাবন করাতে তার পদমর্যাদা বাড়ে না। একজন যা করে, অপরে তার দোষগুণ বিচার করে, এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। সুতরাং ছবির পাশাপাশি তার সমালোচনাও সাহিত্যে দেখা দিতে বাধ্য। এই কারণেই যেদিন থেকে বাংলাদেশে চিত্রকলা আবার নবকলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনকল এবং প্রতিকল সমালোচনা শুরু হয়েছে। এবং এই মতদ্বৈধ থেকে সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে। এই তর্কযুদ্ধে আমার কোনো পক্ষ অবলম্বন করবার সাহস নেই। আমার বিশ্বাস, এদেশে একালের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিত্রবিদ্যায় বৈদ্য এবং আলেখ্যব্যাখ্যানে নিপণতা অতিশয় বিরল, কারণ এ যুগের বিদ্যার মন্দিরে সন্দরের প্রবেশ নিষেধ। তবে বঙ্গদেশের নব্যচিত্র সম্বন্ধে সচরাচর যেসকল আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে, সেগুলি সংগত কি অসংগত তা বিচার করবার অধিকার সকলেরই আছে; কেননা, সেসকল আপত্তি কলাজ্ঞান নয়, সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদূর আমি জানি, নব্যচিত্রকরদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁদের রচনায় বর্ণে-বর্ণে বানান-ভুল এবং রেখায়-রেখায় ব্যাকরণ-ভুল দষ্ট হয়। একথা সত্য কি মিথ্যা শুধু তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁদের চিত্রকর্মের ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মেছে; কিন্তু সে ভাষায় সপণ্ডিত ব্যক্তি বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে দেখতে পাওয়া যায় না, যদিচ ওসকল স্থানে সমালোচকের দর্শন পাওয়া দুলভ নয়। আসল কথা হচ্ছে, এ শ্রেণীর চিত্রসমালোচকেরা অনুকরণ-অর্থে ব্যাকরণ-শব্দ ব্যবহার করেন। এদের মতে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা প্রকৃতির অনুকরণ করেন, সুতরাং সেই অনুকরণের অনুকরণ করাটাই এদেশের চিত্রশিল্পীদের কর্তব্য। প্রকৃতি-নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ-নামক ভূভাগ, এ উভয়ের প্রতি আমার যথােচিত ভক্তিশ্রদ্ধ আছে; কিন্তু তাই বলে তার অনুকরণ করাটাই যে পরমপুরষার্থ, একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি নে। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়, কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আটের ধর্ম। পুরুষের মন প্রকৃতিনর্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়। আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে আমাদের মানসজাত বর মাপজোক যে হবাহব মিলে যেতেই হবে, এমনকোনো নিয়মে আটকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে প্রতিভার চরণে শিকলি পরানো। আটে অবশ্য যথেচ্ছাচারিতার কোনো অবসর নেই। শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্যসামান্য কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য, কিন্তু জ্যামিতি কিংবা গণিতশাস্ত্রের শাসন নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে আমার পূর্বোক্ত মতের যাথার্থের প্রমাণ অতি সহজেই দেওয়া যেতে পারে : একে একে যে দুই হয়, এবং একের পিঠে এক দিলে যে এগারো হয়— বৈজ্ঞানিক হিসেবে এর চাইতে খাঁটি সত্য পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। অথচ একে একে দুই না হয়েও, এবং একের পিঠে একে এগারো না হয়েও, ঐরূপ যোগাযোগে যে বিচিত্র নকশা হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নীচে দেওয়া যাচ্ছে—
সম্ভবত আমার প্রদর্শিত যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ একথা বলতে পারেন যে, ‘চিত্রে আমরা গণিতশাস্ত্রের সত্য চাই নে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্য দেখতে চাই’। প্রত্যক্ষ সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ এবং কলহ যে আবহমান কাল চলে আসছে, তার কারণ অন্ধের হস্তীদর্শন ন্যায়ে নির্নীত হয়েছে। প্রকৃতির যে অংশ এবং যে ভাবটির সঙ্গে যার চোখের এবং মনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তিনি সেইটুকুকেই সমগ্র সত্য বলে ভুল করেন। সত্যভ্রষ্ট হলে বিজ্ঞানও হয় না, আটও হয় না; কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর। কোনো সুন্দরীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসাবে সত্য, তার সৌন্দর্যও তেমনি আর-এক হিসাবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য-নামক সত্যটি তেমন ধরাছোঁয়ার মত পদার্থ নয় বলে সেসম্বন্ধে কোনোরূপ অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। এই সত্যটি আমরা মনে রাখলে নব্যশিল্পীর কৃশাঙ্গী মানসীকন্যাদের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্য অত ব্যগ্র হতুম না; এবং চিত্রের ঘোড়া ঠিক ঘোড়ার মত নয়, এ আপত্তিও উত্থাপন করতুম না; একথা বলার অর্থ–তার অস্থিসংস্থান, পেশীর বন্ধন প্রভৃতি প্রকৃত ঘোড়ার অনরপ নয়। অ্যানাটমি অর্থাৎ অস্থিবিদ্যার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে যে, চিত্রের ঘোটক গঠনে ঠিক আমাদের শকটবাহী ঘোটকের সহোদর নয়, এবং উভয়কে একত্রে জড়িতে জোতা যায় না। এসম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, অস্থিবিদ্যা কঙ্কালের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নয়। কঙ্কালের সঙ্গে সাধারণ লোকের চাক্ষুষ পরিচয় নেই; কারণ দেহতাত্ত্বিকের জ্ঞাননেত্রে যাই হোক, আমাদের চোখে প্রাণীজগৎ কঙ্কালসার নয়। সুতরাং দষ্টজগৎকে অদৃষ্টের কষ্টিপাথরে কষে নেওয়াতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু রূপজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কি মানুষ কি পশ, জীবমাত্রেরই দেহযন্ত্রগঠনের একমাত্র কারণ হচ্ছে উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করা। গঠন যে ক্রিয়াসাপেক্ষ, এই হচ্ছে দেহবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব। ঘোড়ার দেহের বিশেষ গঠনের কারণ হচ্ছে, ঘোড়া তুরঙ্গম। যে ঘোড়া দৌড়বে না, তার অ্যানাটমি ঠিক জীবন্ত ঘোড়ার মত হবার কোনো বৈধ কারণ নেই। পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এবিষয়ে বোধ হয় কোনো মতভেদ নেই। চিত্রাপিত অশ্বের অ্যানাটমি ঠিক চড়বার কিংবা হাঁকাবার ঘোড়ার অনরপ করাতেই বস্তুজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। চলৎশক্তিরহিত অশ্ব, অর্থাৎ যাকে চাবুক মারলে ছিড়বে কিন্তু নড়বে না এহেন ঘোটক, অর্থহীন অনুকরণের প্রসাদেই জীবন্ত ঘোটকের অবিকল আকার ধারণ ক’রে চিত্রকর্মে জন্মলাভ করে। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানসপ্রসত দশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনার নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। তথাকথিত নব্যচিত্র যে নির্দোষ কিংবা নিভুল, এমন কথা আমি বলি না। যে বিদ্যা কাল জন্মগ্রহণ করেছে, আজ যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল সম্পূর্ণ আত্মবশে আসবে, এরূপ আশা করাও বৃথা।
শিল্পহিসাবে তার নানা ত্রুটি থাকা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কোথায় কলার নিয়মের ব্যভিচার ঘটছে, সমালোচকদের তাই দেখিয়ে দেওয়া কর্তব্য। অস্থি নয় বর্ণের সংস্থানে, পেশী নয় রেখার বন্ধনে যেখানে অসংগতি এবং শিথিলতা দেখা যায়, সেইস্থলেই সমালোচনার সার্থকতা আছে। অব্যবসায়ীর অযথা নিন্দায় চিত্রশিল্পীদের মনে শুধু বিদ্রোহীভাবের উদ্রেক করে, এবং ফলে তাঁরা নিজেদের দোষগুলিকেই গুণ ভ্রমে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান।
আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, চিত্র নয়। যেহেতু এ যুগের সাহিত্য চিত্রসনাথ হয়ে উঠেছে, সেই কারণেই চিত্রকলার বিষয় উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। আমার ও-প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার অপর-একটি কারণ হচ্ছে এইটি দেখিয়ে দেওয়া যে, যা চিত্রকলায় দোষ বলে গণ্য তাই আবার আজকাল এদেশে কাব্যকলায় গুণ বলে মান্য।
প্রকৃতির সহিত লেখকদের যদি কোনোরূপ পরিচয় থাকত, তাহলে শুধু বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোজনা করলেই যে বর্ণনা হয়, এ বিশ্বাস তাঁদের মনে জন্মাত না; এবং যে বস্তু কখনও তাঁদের চর্মচক্ষুর পথে উদয় হয় নি, তা
অপরের মনশ্চক্ষর সম্মুখে খাড়া করে দেবার চেষ্টারপ পণ্ডশ্রম তাঁরা করতেন না । সম্ভবত এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, ছবির বিষয় হচ্ছে দশ্যবস্তু, আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদশ্য মন; সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অজনীয় এবং কাব্যকলায় বর্জনীয়। সাহিত্যে সেহাইকলমের কাজ করতে গিয়ে যাঁরা শুধু কলমের কালি ঝাড়েন, তাঁরাই কেবল নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য পূর্বোক্ত মিথ্যাটিকে সত্য বলে গ্রাহ্য করেন। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অন্তদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। দূরদৃষ্টি লাভ করার অর্থ চোখে চালশে-ধরা নয়। দেহের নবদ্বার বন্ধ করে দিলে মনের ঘর অলৌকিক আলোকে কিংবা পারলৌকিক অন্ধকারে পণ হয়ে উঠবে বলা কঠিন। কিন্তু সব লোকবিদিত সহজ সত্য এই যে, যাঁর ইন্দ্রিয় সচেতন এবং সজাগ নয়, কাব্যে কৃতিত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার অপপ্রয়োগে যাঁদের চক্ষু উন্মীলিত না হয়ে কানা হয়েছে, তাঁরাই কেবল এ সত্য মানতে নারাজ হবেন। প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার, বাছাই করবার এবং ভাষায় সাকার করে তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি। বজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপরেই কবিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত। মহাকবি ভাস বলেছেন যে, ‘সুনিবিষ্ট লোকের রূপে বিপর্যয় করা’ অন্ধকারের ধর্ম। সাহিত্যে ওরূপ করাতে প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হয় না; কারণ প্রতিভার ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ করা, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা–প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষ করা নয়। অলংকারশাস্ত্রে বলে, অপ্রকৃত অতিপ্রকৃত এবং লৌকিকজ্ঞান-বিরদ্ধে বর্ণনা কাব্যে দোষ হিসেবে গণ্য। অবশ্য পৃথিবীতে যা সত্যই ঘটে থাকে, তার যথাযথ বর্ণনাও সব সময়ে কাব্য নয়। আলংকারিকেরা উদাহরণস্বরূপ দেখান যে, ‘গৌ তৃণং অত্তি’ কথাটা সত্য হলেও ওকথা বলায় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাই বলে ‘গোররা ফলে ফলে মধপান করছে’ এরূপ কথা বলাতে, কি বতুজ্ঞান কি রসজ্ঞান, কোনোরূপ জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। এথলে বলে রাখা আবশ্যক যে, নিজেদের সকলপ্রকার এটির জন্য আমাদের পবপুরুষদের দায়ী করা বর্তমান ভারতবাসীদের একটা রোগের মধ্যে হয়ে পড়েছে। আমাদের বিশ্বাস, এ বিশ্ব নবর এবং মায়াময় ব’লে আমাদের পবপুরুষরা বাহ্যজগতের কোনোরূপ খোঁজখবর রাখতেন না। কিন্তু একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা কস্মিনকালেও অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলে ভুল করেন নি, কিংবা একলক্ষে যে মনের পূর্বোক্ত প্রথম অবস্থা হতে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়— এরূপ মতও প্রকাশ করেন নি। বরং শাস্ত্র এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, অপরাবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলে কারও পক্ষে পরাবিদ্যা লাভের অধিকার জন্মায় না; কেননা, বিরাটের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বরাটের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়। আসল কথা হচ্ছে, মানসিক আলস্যবশতই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ। আমরা যে কথায় ছবি আঁকতে পারি নে, তার একমাত্র কারণ আমাদের চোখ ফোটবার আগে মুখ ফোটে।
একদিকে আমরা বাহ্যবস্তুর প্রতি যেমন বিরক্ত, অপরদিকে অহং-এর প্রতি ঠিক তেমনি অনুরক্ত; আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের মনে যেসকল চিন্তা ও ভাবের উদয় হয়, তা এতই অপর্ব এবং মহার্ঘ যে, স্বজাতিকে তার ভাগ না দিলে ভারতবর্ষের আর দৈন্য ঘুচবে না। তাই আমরা অহর্নিশি কাব্যে ভাবপ্রকাশ করতে প্রস্তুত। ঐ ভাবপ্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশি থাক না, অপরের কাছে তার যা-কিছু মূল্য সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব ম’রে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত, তাহলে আমরা শিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না। মানুষমাত্রেরই মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়–এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করবার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা। কবি যদি নিজেকে বীণাহিসেবে না দেখে বাদকহিসেবে দেখেন, তাহলে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ করবার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায়। এবং যে মহত থেকে কবিরা নিজেদের পরের মনোবীণার বাদকহিসেবে দেখতে শিখবেন, সেই মহত থেকে তাঁরা বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হবার সার্থকতা বুঝতে পারবেন। তখন আর নিজের ভাববস্তুকে এমন দিব্যরত্ন মনে করবেন না যে, সেটিকে আকার দেবার পরিশ্রম থেকে বিমুখ হবেন। অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিস নয়, একথা গণধর্মাবলম্বীরা সহজে মানতে চান না। এই কারণেই এত কথা বলা।
আমার শেষ বক্তব্য এই যে, ক্ষদ্রত্বের মধ্যেও যে মহত্ত্ব আছে, আমাদের নিত্যপরিচিত লৌকিক পদার্থের ভিতরেও যে অলৌকিকতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তার উদ্ধারসাধন করতে হলে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে হলে সাধনার আবশ্যক; এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে, দেহমনকে বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা। যাঁর চোখ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শনলাভের জন্য শিবনেত্র হন; এবং যাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতা লাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নব্যলেখকদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন দেশী বিলেতি কোনোরূপ বুলির বশবর্তী না হয়ে, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করবার জন্য ব্রতী হন। তাতে পরের না হোক, অন্তত নিজের উপকার করা হবে।
আশ্বিন ১৩২০
বর্তমান বঙ্গসাহিত্য
অনেকে বলে থাকেন যে, আমাদের সাহিত্যের সত্যযুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গেই এ দেশ থেকে অন্তর্ধান হয়েছে। এখন ঘোর কলি, কেননা এ যুগে সাহিত্যের যে একটিমাত্র পদ অবশিষ্ট আছে সে হচ্ছে সমালোচনা এবং আমাদের যতকিছু লাফঝাঁপি সেসব ঐ এক পায়ের উপর, তার পর ভবিষ্যতে যখন উক্ত পদের আস্ফালন বন্ধ হবে, তখন মন্বন্তর। এসব কথা শুনে আমি হতাশ হয়ে পড়ি নে, কেননা অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালোবাসা দুইই বেশি আছে। আমরা ইভলিউশন-পন্থী; সুতরাং আমাদের সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই, সুমুখে গড়ে উঠেছে। আমাদের কল্পিত ধরার স্বর্গ অতীতের ভুই ফুড়ে উঠবে না, বর্তমানের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং আমাদের কাছে অতীতের অপেক্ষা বর্তমান ঢের বেশি মূল্যবান। অতীতের সাহায্যে আমরা বড়জোর বর্তমানের ব্যাখ্যা করতে পারি, তাও আবার অংশিক ভাবে, কিন্তু বর্তমানের সাহায্যে আমরা ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি। আবিষ্কার করার চাইতে নির্মাণ করা যে-পরিমাণে শ্রেষ্ঠ অতীতের জ্ঞানের চাইতে বর্তমানের জ্ঞান লাভ করা সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ বর্তমানকেই সবচাইতে কম চেনে এবং কম জানে। এ পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত তাই সবচেয়ে অপরিচিত। যা চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের চোখের সুমুখে থাকে, তার দিকে আমরা বড়-একটা দৃষ্টিপাত করি নে। ঐ কারণেই বর্তমানের চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না এবং তার রূপ আমাদের মনে ধরে না। তা ছাড়া বর্তমান একটি প্রবাহ, দিনের পর দিন হচ্ছে কালের ঢেউয়ের পরে ঢেউ, সুতরাং এ বর্তমানের ইয়ত্তা করতে হলে কালের ঢেউ গুনতে হয় না। অপর পক্ষে অতীত হচ্ছে একটি জমাট নিরেট জড় পদার্থ, তার চারি দিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করা যায়। সুতরাং অতীতের গুণকীর্তন করা নেহাত সহজ, বিশেষতঃ চোখ বুজে। আর-এক কথা, স্বদেশের অতীত হচ্ছে প্রতি জাতির পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি এবং তা সমাজের ভোগদখলের বিষয়, অতএব তার প্রতি সাংসারিক মনের টানও বেশি মানও বেশি। বর্তমানের দুর্ভাগ্য এই যে, তা অস্থাবর। এবং তার যা ভোগ সে শুধু –কর্মভোগ। এই কারণে বর্তমানকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায় না। বর্তমান সাহিত্য হচ্ছে বর্তমানেরই একটি অঙ্গ, কাজেই বর্তমান সাহিত্যিকরা পেঁয়ো যোগীর ন্যায় সমাজের কাছে ভক্তি পাওয়া দূরে থাক্, ভিখও পান না। অথচ এই উপেক্ষিত বর্তমানই যখন আমাদের অদূর-ভবিষ্যতের নির্ভরস্থল, তখন এ যুগের সাহিত্যের যথাসম্ভব পরিচয় নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। চেষ্টা করলে হয়তো এর ভিতর থেকেও একটা আশার চেহারা বার করা যেতে পারে।
আমাদের পক্ষে নবসাহিত্যের নিন্দা করা যেমন সহজ, প্রশংসা করা তেমনি কঠিন। কেননা খ্যাতনামা লেখকদের বিচার করবার অধিকার যেখানে কারও নেই, সেখানে অখ্যাতনামা লেখকদের উপরে জজ, হয়ে বসবার অধিকার। সকলেরই আছে। জন্মাবধি উঠতে বসতে খেতে শুতে যে বস্তুর সুখ্যাতি শুনে আসছি, সে বস্তু যে মহার্ঘ এ বিশ্বাস অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে। যায়। গুরুজনদের তৈরি মত আমরা বিনা বাক্যে মেনে নিই, কেননা তা মেনে নেবার ভিতর মনের কোনো খাটুনি নেই। যদি আমরাই চিন্তামার্গে ক্লেশ করব, তাহলে গুরুর দরকার কি। আর যদি আমরাই পূজা করব তাহলে পুরোহিতের দরকার কি। কেননা গুরুপুরোহিতেরা সমাজের হাতেগড়া, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক labour-saving machines। নবসাহিত্যের দুর্ভাগ্যই এই যে, তা অতীতের ডিপ্লোমা নিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত। হয় না; এ সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হলে নিজের অনুভূতি দিয়ে তা যাচাই করতে হয়, নিজের বুদ্ধি দিয়ে তা পরীক্ষা করতে হয়। আমরা ক’জনে সে পরিশ্রমটুকু করতে রাজি? সুতরাং নবসাহিত্যের প্রশংসার চাইতে নিন্দাই যে বেশির ভাগ শোনা যায়, তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। এইসকল নিন্দাবাদের বিচার সূত্রেই আমরা প্রকারান্তরে নবসাহিত্যের গুণাগুণের বিচার করতে চাই।
নবসাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অপর্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন ও প্রতিভাহীন, চুটকি ও নকল। আমি একে একে এইসকল অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।
নবসাহিত্যের পরিমাণ যে অপর্যাপ্ত তা অস্বীকার করবার জো নেই। বর্তমানে এত নিত্যনূতন পুস্তক এবং পুস্তিকা, পত্র এবং পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হচ্ছে যে, এ যুগের তুলনায় বঙ্গদর্শনের যুগের বঙ্গসরস্বতীকে বন্ধ্যা বললেও অত্যুক্তি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নামে এই অপবাদ ছিল যে, বাঙালি রসনাসর্বস্ব, বিংশ শতাব্দীতে আমরা যদি কিছু হই তো রচনাসম্ব। এমনকি এই নব যুগধর্মের শাসনে গত যুগের অনেক পাকা বক্তারা বেঁচে আবার লেখক হয়ে উঠছেন, নইলে যে তাদের গাদে পড়ে থাকতে হয়।
এক কথায়, আজকের দিনে বাংলার সাহিত্যসমাজ লোকে লোকারণ্য; এবং এ জনতার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আছেন। বঙ্গসাহিত্যের মন্দিরে বঙ্গমহিলারা যে শুধু প্রবেশ লাভ করেছেন তা নয়, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছেন। বসেছেন বলা বোধ হয় ঠিক হল না, কারণ এ স্থলে এরা বসে নেই, পুরুষদের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলছেন। ইংরেজি রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে peaceful penetration, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে স্ত্রীজাতি আমাদের সাহিত্যরাজ্য ধীরে ধীরে এতটা দখল করে নিচ্ছেন যে, আমার সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয় যে, এ রাজ্য হয়তো ক্রমে নারীরাজ্য হয়ে উঠবে। এ আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নয়, তার প্রমাণ গত মাসের ‘ভারতবর্ষে’র প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। সাহিত্যসমাজের এই পরদাপার্টিতে অন্ততঃ চল্লিশ জন ভদ্রমহিলা যোগদান করেছিলেন। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা নেই, সে দেশে স্ত্রীসাহিত্যের এতটা প্রসার ও পশার বৃদ্ধির ভিতর কি একটু রহস্য নেই? এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, এই নবসাহিত্যের মূলে এমনএকটি অজ্ঞাত অবাধ্য এবং অদম্য শক্তি নিহিত রয়েছে, যার স্মৃতি কোনোরূপ বাহ ঘটনার অধীন নয়? বালিকাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয় স্থলেই নবসাহিত্য যে সমভাবে ও সমতেজে অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হচ্ছে, এর থেকে বোঝ উচিত যে, আমাদের জাতীয় মন কোনো নৈসর্গিক কারণে সহসা অসম্ভব রকম উর্বর হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে আশার বীজ বপন করাই সংগত, নিরাশার নয়ন-অসার নয়।
এ স্থলে নিজের কৈফিয়তস্বরূপে একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক। কেউ মনে করবেন না যে, আমি লেখিকাদের উপর কোনোরূপ কটাক্ষ করে এসব কথা বলছি। কেননা তাঁদের রচিত সাহিত্যে এক স্বাক্ষর ব্যতীত স্ত্রীহস্তের অপর কোনো চিহ্ন নেই। ওসব লেখা শ্ৰী-স্বাক্ষরিত হলে তার থেকে ‘মতী-ভ্রংশতার পরিচয় কেউ পেতেন না। এ দেশে স্ত্রী-পুরুষের যে কোনো প্রভেদ আছে তা বঙ্গসাহিত্য থেকে ধরবার জো নেই।
এত বেশি লোক যে এত বেশি লিখছে, তাতে আনন্দিত হবার অপর কারণও আছে। এই অজস্র রচনা এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বাঙালি জাতি এ যুগে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। যদি কেউ এ স্থলে এ কথা বলেন যে, বাঙালির রচনা যে-পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে সে-পরিমাণে কিছুই প্রকাশ করছে না, তার উত্তরে আমি বলব যে, বাঙালির জাতীয় আত্মা আজও গড়ে ওঠে নি এবং সে আত্ম গড়ে তোলবার পক্ষে সাহিত্য একমাত্র না হলেও একটি প্রধান উপায়। মানুষের দেহ যেমন দৈহিক ক্রিয়াগুলির চর্চার সাহায্যে গড়ে ওঠে, মানুষের মনও তেমনি মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে গড়ে ওঠে। জাতীয় আত্মা আবিষ্কার করবার বস্তু নয়, নির্মাণ করবার বস্তু। আত্মাকে প্রকাশ করবার উদ্যম এবং প্রযত্ন থেকেই আত্মার আবির্ভাব হয়, কেননা সৃষ্টি বহির্মুখী। অবশ্য আমি তাই বলে এ দাবি করি নে যে, আজকাল যত কথা ছাপায় উঠছে তার সকল কথাই জাতীয় মনের উপর ছাপ রেখে যাবে। সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর’ ভারতচন্দ্রের এ উক্তি ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষে তেমনি সত্য। সুতরাং বাঙালি জাতি যে অনেক বাক্য বৃথা ব্যয় করছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে কথা বলবার কোনো অবশ্যকতা ছিল না সে কথা বলা হয়েছে বলেই যে তা টিকে যাবে, এমন ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। সাহিত্যজগৎও যোগ্যতরের উবর্তনের নিয়মের অধীন। কালের নির্মম কবলে পড়ে যা ক্ষীণজীবী তা অচিরে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই হবে। তবে বহু লোকে বহু কথা বললে অনেক সত্য কথা উক্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নানা মুনির নানা মত থাকাটা দুঃখের বিষয় নয়, নানা মুনির মতের ঐক্যটাই সাহিত্যসমাজে আসল দুঃখের বিষয়। কেননা সে মত যদি ভুল হয় তাহলে সাহিত্যের ষোলো কড়াই কানা হয়ে যায়। এবং মুনিদের যে মতিভ্রম হয় এ কথা সংস্কৃতেও লেখা আছে। এ যুগের বঙ্গসরস্বতী বহুভাষী হলেও যে বহুরূপী নন এ তত প্রত্যক্ষ সত্য। তবে আমাদের সাহিত্যের সুর যে একঘেয়ে তার কারণ আমাদের জীবন বৈচিত্র্যহীন, এবং এই বৈচিত্র্যহীনতার চর্চা আমরা একটা জাতীয় আর্ট করে তুলেছি। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, আমাদের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, নানা যন্ত্র এক সুরে বেঁধে তাতে এক সুর বাজালেই ঐকতান হয়। আর্ট-জগতে এই অদ্বৈতবাদের হাত থেকে উদ্ধার না পেলে বঙ্গসাহিত্য মুক্তিলাভ করবে না, এবং যতদিন এ দেশে আবার নূতন চৈতন্যের আবির্ভাব না হবে ততদিন আমরা এক কথাই এক শ বার বলব, কেননা সে কথা বলার ভিতরেও মন নেই, শোনার ভিতরেও মন নেই। তাই বলে আমাদের সকল লেখাপড়া একেবারেই অনর্থক নয়। আমরা আর-কিছু করি আর না করি ভাবী গুণীর জন্য আসর জাগিয়ে রাখছি। পাঠকসমাজকে ঘুমিয়ে পড়তে না দেওয়াটাও একটা কম কাজ নয়।
আমরা সদলবলে সাহিত্য তৈরি করি আর না করি, সদলবলে পাঠক তৈরি করছি।
পূর্বে যা বলা গেল, তা অবশ্য সকলের সমান মনঃপূত হবে না, কিন্তু এ কথা আপনারা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, যে ক্ষেত্রে লেখকের সংখ্যা। অগণ্য, সে ক্ষেত্রে কোনো লেখক-এর সাহিত্য-দ্রুম স্বরূপে গ্রাহ্য হবেন না। এ বড় কম লাভের কথা নয়। হাজার অপ্রিয় হলেও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের কোনো কোনো এরও এমন মহাবোধিবৃক্ষত্ব লাভ করেছিলেন যে, অদ্যাবধি বঙ্গসাহিত্যের পুরোনো পাণ্ডারা তাঁদের গায়ে সিদুর লেপে অপরকে পূজা করতে বলেন। অমুকে কি লিখেছেন কেউ না জানলেও তিনি যে একজন বড় লেখক তা সকলেই জানেন, এমন প্রথিতযশা প্রবীণ সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে বিরল নয়।
এ সাহিত্যের বিরুদ্ধে চুটকিত্বের যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে অপবাদের সত্যাসত্য একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ছোট গল্প, খণ্ড কবিতা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং প্রক্ষিপ্ত দর্শনই এ সাহিত্যের প্রধান সম্বল। সমালোচকদের মতে এই কৃশতাই হচ্ছে এ সাহিত্যের দুর্বলতার লক্ষণ। বিংশ শতাব্দীতে যে কোনো নূতন মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার কিংবা শকুন্তলাতত্ত্ব লেখা হয় নি, এ কথা সত্য। এ যুগের কবিদের বাহু যে আজানুলম্বিত নয়, তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। বধ এবং সংহার ছাড়া কাব্যের যে অপর কোনো কর্তব্য নেই, এ কথা একালে মানা কঠিন। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে, মার্কা ব্যাপার না থাকলে কাব্য মহাকাব্য হয় না। তাহলে বলতে হয় যে, সাহিত্যজগতের এমন কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই যার দরুন যুগে যুগে সকলকে শুধু মহাকাব্যই লিখতে হবে। প্যারাডাইস লস্ট -এর পরে ইংরেজি ভাষায় আর দ্বিতীয় মহাকাব্য লেখা হয় নি, এবং ফরাসি ভাষায় ও-শ্রেণীর কাব্য কস্মিকালেও রচিত হয় নি, তাই বলে ফরাসি সাহিত্য এবং মিল্টনের পরবর্তী ইংরেজি সাহিত্যের যে কোনোরূপ গৌরব নেই, এ কথা বলবার দুঃসাহস কোনো পাশ্চাত্ত্য সমালোচক তাদের রক্তমাংসের শরীরে ধারণ করেন না।
তার পর আমরা যে শকুন্তলার চাইতে দ্বিগুণ বড় শকুন্তলাতত্ত্ব রচনা করি নে, তার জন্য আমাদের কাছে পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুর সার, অতএব সংক্ষিপ্ত। এ বিশ্বটি এত বিরাট যে, তাকে সচরাচর অনন্ত ও অসীম বলা হয়ে থাকে, অথচ তাত্ত্বিকেরা বিশ্বতত্ত্ব দু-চারটি ক্ষীণ সূত্রেই আবদ্ধ করে থাকেন। সুতরাং আমরা কোনো সৃষ্ট পদার্থের বিষয়ে দু শ হাত তত্ত্বজাল বুনতে সাহসী হই নে, অন্ততঃ কোনো কাব্যরত্নকে সে জালে জড়াতে চাই নে। কাব্যের আগুনের পরিচয় দেবার জন্য তাকে সমালোচনার ছাইচাপা দেওয়াটা সুবিবেচনার কার্য নয়, কেননা সে গুণের পরিচায়ক হচ্ছে অনুভূতি।
এ যুগের রচনার নাতিদীর্ঘ এই সত্যেরই প্রমাণ দেয় যে, একালের লেখকেরা পাঠকদের মান্য করতে শিখেছেন। হিন্দুস্থানিরা বলেন যে, ‘আক্কেলিকো ইসারা বাস। যাদের শ্রোতার আক্কেলের উপর কোনো আস্থা নেই, তারাই একটুখানি কথাকে ফেনিয়ে ফাপিয়ে ফুলিয়ে অনেকখানি করে তুলতে ব্যস্ত।
সমালোচকদের মতে বর্তমানের আর-একটি অপরাধ এই যে, এ যুগে এমন কোনো লেখক জন্মগ্রহণ করেন নি, যার প্রতিভায় দেশ উজ্জ্বল করে রেখেছে। এ আমাদের দুর্ভাগ্য, দোষ নয়; প্রতিভার জন্মের রহস্য কোনো দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক অদ্যাবধি উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। তবে এটুকু আমরা জানি যে, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য চাই। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, নূতন সাহিত্য গড়বার যে সুযোগ গত শতাব্দীর লেখকেরা পেয়েছিলেন, সে সুযোগ আমরা অনেকটা হারিয়েছি।
গত যুগের লেখকেরা সবাই প্রধান না হোন, সবাই স্বাধীন ছিলেন। তৎপূর্ব-যুগের বঙ্গসাহিত্যের চাপের ভিতর থেকে তাদের তেড়েফুড়ে বেরতে হয় নি। একটি সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রভূত ঐশ্বর্য–ও অপূর্ব সৌন্দর্য–শালী সাহিত্যের সংস্পর্শে ই উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য জন্মলাভ করে। সে সাহিত্যের উপর প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের বঙ্গসাহিত্যের কোনোরূপ প্রভুত্ব ছিল না। অন্নদামঙ্গলের ভাষা ও ছন্দের কোনোরূপ খাতির রাখলে মাইকেল মেঘনাদবধ রচনা করতেন না, এবং বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনীর কোনোরূপ খাতির রাখলে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনা করতেন না। মিল্টন এবং স্কট যাদের গুরু, তাঁদের কাছে ভারতচন্দ্রের ঘেঁষবার অধিকার ছিল না।
কিন্তু আজকের দিনে ইংরেজি সাহিত্য আমাদের কাছে এতটা পরিচিত এবং গা-সওয়া হয়ে এসেছে যে, তার থেকে আমরা আর বিশেষ কোনো নূতন। উদ্দীপনা কিংবা উত্তেজনা লাভ করি নে। আমাদের মনে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম পরিচয়ের চমক ভেঙেছে, কিন্তু বিশেষ পরিচয়ের প্রভাব স্থান পায় নি। সুতরাং আমরা গত যুগের সাহিত্যেরই জের টেনে আসছি। আমাদের পক্ষে তাই নতুন কিছু করা একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিভাশালী লেখকের সাক্ষাৎ আমরা সেই যুগে পাই, যে যুগে একটা নূতন এবং প্রবল ভাবের প্রবাহ হয় ভিতর থেকে ওঠে নয় বাইরে থেকে আসে। গত যুগে যে ভাবের জোয়ার বাইরে থেকে এসেছিল, এ যুগে তার তোড় এত কমে এসেছে যে, ভাটা শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। এদিকে ভিতর থেকেও একটা নূতন কোনো ভাবের উৎস খুলে যায় নি। বরং সমাজের মনের টান আজ পুরাতনের দিকে, এও তো ভাবের প্রবাহের ভাটার অন্যতম লক্ষণ। এই ভাটার মুখে নতুন কিছু করতে হলে কালের স্রোতের উজান বইতে হয়। তা করা সহজ নয়। এ অবস্থায় যা করা সহজ তা হচ্ছে সনাতন জ্যাঠামি। সুতরাং নবসাহিত্যকে বিশেষত্বহীন এবং প্রতিভাহীন বলায় সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না। আরও বিপদের কথা এই যে, আমরা উভয়সংকটে পড়েছি। কেননা যদি আমরা গত শতাব্দীর সাহিত্যের অনুসরণ করি, তাহলে সমালোচকদের মতে আমরা নকল সাহিত্য রচনা করি। আর যদি অনুকরণ না করি, তাহলে পূর্বোক্ত মতে আমরা কাব্যের উচ্চ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হই। অথচ আসল ঘটনা এই যে, নবযুগ কতক অংশে পূর্ব যুগের অধীন এবং কতক অংশে স্বাধীন। এই কারণে নবীন সাহিত্যিকেরা গত যুগের সাহিত্যের কোনো কোনো অংশের অনুকরণ করতে অক্ষম এবং কোনো কোনো অংশের অনুসরণ করতে বাধ্য। একালে যে মেঘনাদবধ কিম্বা দুর্গেশনন্দিনীর অনুকরণে গদ্য এবং পদ্য কাব্য রচিত হয় না, তার কারণ বাঙালি জাতির মনের কলে স্কট মিল্টন মিল ও কঁং-এর চাবির দম ফুরিয়ে এসেছে। অপর পক্ষে বর্তমান কাব্যসাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে অতিবিস্তৃত এবং অপ্রতিহত, তা অস্বীকার করবার জোও নেই, প্রয়োজনও নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বর্তমান কাব্যসাহিত্যের একমাত্র আদর্শ বলে যে সে-সাহিত্যের কোনো মূল্য কিংবা মর্যাদা নেই এ কথা বলায় শুধু স্কুলদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়। সুতরাং নবসাহিত্যকে নকল সাহিত্য, বলার কি সার্থকতা আছে, তাও একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার।
সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, পরের লেখার অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করে সাহিত্য রচনা করা যায় না। এ কথাটা ষোলো আনা সত্য নয়। ও উপায়ে অবশ্য কালিদাস হওয়া যায় না, কিন্তু শ্রীহর্ষ হওয়া যায়। রত্নাবলী মালবিকাগ্নিমিত্রের ছাঁচে ঢালা, অথচ সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি উপাদেয় নাটক। পৃথিবীর মহাপ্রাণ কবিদের স্পর্শে বহু লেখক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন, এবং এই কারণেই তাদের অবলম্বন করেই সাহিত্যের নানা স্কুল গড়ে ওঠে। ফরাসি এবং জর্মান সাহিত্যে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্যেটের আনুগত্য স্বীকার করাতে শিলারের প্রতিভার হ্রাস হয় নি। ভিক্টর হুগোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসসে Musset অ-কবির দেশে গিয়ে পড়েন নি। এবং ফ্লোবেয়রের কাছে শিক্ষানবিশি করার দরুন গী দ্য মোপাসাঁর গল্প সাহিত্যসমাজে উপেক্ষিত হয় নি। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও এরূপ ঘটনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাকে আমরা বৈষ্ণব কবিতা বলি, তা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর। অনুকরণেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস লোচনদাস অনন্তদাসের রচনার যে কোনো মূল্য নেই, এ কথা কোন সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে, পর-সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য গঠিত হয় না, তাহলে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় সাহিত্য রচিত হয় নি—কেননা গত শতাব্দীর মধ্যযুগের গল্প এবং উপন্যাস, কাব্য এবং মহাকাব্য, সবই যে-সাহিত্যের অনুকরণে রচিত হয়েছিল, সে-সাহিত্য আমাদের নিতান্তই পর; তা অপর দেশের অপর জাতের অপর ভাষায় লিখিত। এ সত্ত্বেও আমরা গত যুগের এই আহেলা বিলাতি সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্য বলে আদর করি। তার কারণ এই যে, যে সাহিত্য উপর-সাহিত্য, তা অপরই হোক আর আপনই হোক, মানবমনের উপর তার প্রভাব অনিবার্য।
সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে এবং অনুসরণে যে কাব্যসাহিত্য রচিত হয়েছে, তা নকল সাহিত্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।
এই নবকবিদের রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এসকল রচনা ভাষার পরিপাট্যে এবং আকারের পরিচ্ছিন্নতায় পূর্বযুগের কবিতার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যেমন কেবলমাত্র মনের আনন্দে গান গাইলে তা সংগীত হয় না, তেমনি কেবলমাত্র মনের আবেগে স্বচ্ছন্দে লিখে গেলেও তা কবিতা হয় না। মনের ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতার নামই রচনাশক্তি। মনের ভাবকে গড়ে না তুলতে পারলে তা মূর্তিধারণ করে না আর যার মূর্তি নেই তা অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হতে পারে না। কবিতা শব্দকায়। ছন্দ মিল ইত্যাদির গুণেই সে কায়ার রূপ ফুটে ওঠে। মনোভাবকে তার অনুরূপ দেহ দিতে হলে শব্দজ্ঞান থাকা চাই, ছন্দমিলের কান থাকা চাই। এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য সাধনা চাই, কেননা সাধনা ব্যতীত কোনো আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না। নবকবিরা যে সে-সাধনা করে থাকেন তার কারণ এ ধারণা তাঁদের হৃদয়ংগম হয়েছে যে, লেখা জিনিসটে একটা আর্ট। নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের ‘কবিতাবলী’ কিংবা নবীনচন্দ্রের ‘অবকাশঞ্জিনী’র তুলনা করলে নবযুগের কবিতা পূর্বযুগের কবিতার অপেক্ষা আর্ট-অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে এ শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউশনের এক ধাপ উপরে উঠে গেছে। এ স্থলে হয়তো পূর্বপক্ষ এই আপত্তি উত্থাপন করবেন যে, ভাবের অভাব থেকেই ভাষার এইসব কারিগরি জন্মলাভ করে। যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য নেই, তার যে আত্মার ঐশ্বর্য আছে, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারি নে। এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে ভাবের দিব্যমূর্তি দেখবার মত অন্তদৃষ্টি আমার নেই। প্রচ্ছন্ন মূতি ও পরিচ্ছিন্ন মূর্তি এক রূপ নয়। ভাব যে কাব্যের আত্মা এবং ভাষা তার দেহ, এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাব্যের দেহ থেকে আত্মা পৃথক্ করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় দেহের শেষ হয় এবং আত্মার সূত্রপাত হয়, সে সন্ধান কোনো দার্শনিকের জানা নেই। যাঁর রসজ্ঞান আছে তার কাছে এসব তর্কের কোনো মূল্য নেই। কবিতারচনার আর্ট নবীন কবিদের অনেকটা করায়ত্ত হয়েছে, এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে তাদের লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। ভারতচন্দ্র মালিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে–
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।
স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কবিতার যদি ঠাট বাদ দেওয়া যায়, তাহলে যে গুঁড়া অবশিষ্ট থাকে তাতে ফোঁটা দেওয়াও চলে না, কেননা সে গুঁড়া চন্দনের নয়। অথচ ভারতচন্দ্র যে কবি, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। নবীন কবিদের যে ভাবসম্পদ নেই, এ কথা বলায়, আমার বিশ্বাস, কেবলমাত্র অন্যমনস্কতার পরিচয় দেওয়া হয়। মহাকবি ভাস বলেছেন যে, পৃথিবীতে ভালো কাজ করবার লোক সুলভ, চেনবার লোকই দুর্লভ।
মহাকাব্যের দিন যে চলে গেছে, তার প্রমাণ বর্তমান ইউরোপেও পাওয়া যায়। সে দেশে কবিতা আজও লেখা হয়ে থাকে, কিন্তু হাতে-বহরে সে সবই ছোট। ফরাসিদেশের বিখ্যাত লেখক আঁদ্রে জী বলেন যে, গীতাঞ্জলি মুষ্টিমেয় না হলে বর্তমান ইউরোপ তা করজোড়ে গ্রহণ করত না। তার ধারণা। ছিল যে, ভারতবর্ষে রামায়ণ-মহাভারতের চাইতে ছোট কিছু লেখা হয় নি এবং হতে পারে না। এ কথা অবশ্য সত্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন এক দিকে রামায়ণ-মহাভারত আছে, অপর দিকে তেমনি দু-লাইন চার-লাইন কবিতারও। ছড়াছড়ি। ভারতবর্ষে পূর্বে যা ছিল না, সে হচ্ছে এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন পদার্থ। একালে আমরা যে ব্যাস-বাল্মীকির অনুকরণ না করে অমরু-ভর্তৃহরির অনুসরণ করি, সে যুগধর্মের প্রভাবে। যে কারণে ইউরোপে আর মহাকাব্য লেখা হয় না সেই একই কারণে এ দেশেও মহাকাব্য লেখা স্থগিত রয়েছে। এ যুগের কবিতা হচ্ছে হৃদয়ের স্বগতোক্তি, সুতরাং সে উক্তি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাইতে দীর্ঘ হতে পারে না। কিন্তু একালে গল্প আমরা গদ্যে বলি, কেননা আমরা আবিষ্কার করেছি যে, দুনিয়ার কথা দুনিয়ার লোকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য গদ্যের পথই প্রশস্ত। সুতরাং গল্পের উত্তরোত্তর দেহ সংকুচিত হওয়াটা ক্রমোন্নতির লক্ষণ নয়। ইউরোপে আজও গদ্যে এমন-এমন নভেল লেখা হয়ে থাকে, যা আকারে মহাভারতের সমান না হলেও রামায়ণের তুল্যমূল্য। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নভেলিস্ট টলস্টয়ের এক-একখানি নভেল এক-একখানি মহাকাব্যবিশেষ। ও দেশের গদ্যসাহিত্যে যেমন এক দিকে ব্যাস-বাল্মীকি আছে, অপর দিকে তেমনি অমরু-ভর্তৃহরিরও অভাব নেই। যে ক্ষেত্রে হাজার হাজার পাতার দু-চারটি গল্প জন্মলাভ করছে, সেই ক্ষেত্রেই আবার দু-পাতা চার-পাতার হাজার হাজার গল্প জন্মলাভ করছেএতেই পরিচয় দেয় যে, ইউরোপের মনের ক্ষেত্র কত সরস কত সতেজ কত উর্বর। সুতরাং আমাদের নব গদ্যসাহিত্যে যে ছোটগল্প ছাড়া আর কিছু গজায় না তাতে অবশ্য এ সাহিত্যের দৈন্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু এ দীনতা ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় যতটা ধরা পড়ে, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের তুলনায় ততটা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে গত যুগের গল্পসাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্রের কণ্ঠমালা এবং তারক গাঙ্গুলির স্বর্ণলতা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এ যুগের গল্পলেখকেরা যে সাধারণতঃ ছোটগল্প রচনার পক্ষপাতী তার কারণ এই যে, আমাদের জীবন ও ও মন এতই বৈচিত্র্যহীন এবং সে মনে ও সে জীবনে ঘটনা এত অল্পই ঘটে, এবং যা ঘটে তাও এতটা বিশেষত্বহীন যে, তার থেকে কোনো বিরাট কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করা যায় না। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে অ্যানাক্যারেনিনা কিংবা লে মিজারেবল গড়তে বসায় বাচালতার পরিচয় দেওয়া হয়, প্রতিভার নয়।
এ সমাজে যা পাওয়া যায়, এবং সম্ভবতঃ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে হচ্ছে ছোটগল্পের খোরাক। আমাদের জীবনের রঙ্গভূমি যতই সংকীর্ণ হোক-না কেন, তারই মধ্যে হাসিকান্নার অভিনয় নিত্য চলছে, কেননা আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব করেও নিজেদের মানুষ ছাড়া অপর কোনো শ্রেণীর জীবে পরিণত করতে পারি নি। ভয়-আশা উদ্যম-নৈরাশ্য ভক্তি-ঘৃণা মমতা-নিষ্ঠুরতা ভালোবাসা-দ্বেষহিংসা বীরত্ব-কাপুরুষতা, এক কথায় যা নিয়ে এই মানবজীবন, তা মিনিয়েচারে এ সমাজে সবই মেলে। সুতরাং যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের গল্পসাহিত্যের এই নূতন পথটি খুলে দিলেন তখন আমরা দলে দলে সোৎসাহে সেই পথে এসে পড়লুম। এ অবশ্য আপসোসের কথা নয়। এবং এর জন্যও দুঃখ করবার দরকার নেই যে, এ পথে এখন এমন বহু লোক দেখা যায়, যাদের কাজ হচ্ছে শুধু সে পথের ভিড় বাড়াননা। কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, কোনো মহাজন কর্তৃক একটি নুতন পন্থা অবলম্বিত হলে সেখানে চিরদিনই এমনি জনসমাগম হয়ে থাকে, তার মধ্যে দু-চারজন শুধু এগিয়ে যান। এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, সে পথ বিপথ; কিন্তু এই প্রমাণ হয় যে, বেশির ভাগ লোক দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। Many are called but few are chosen, বাইবেলের এ কথা হচ্ছে এ সম্বন্ধে শেষ কথা। এ যুগে কোনো অসাধারণ প্রতিভাশালী উপন্যাসিকার না থাকলেও এমন অনেক গল্প লেখা হয়ে থাকে যা গত শতাব্দীর কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের কলম হতে বেরত না। সুতরাং নবসাহিত্যে যদি chosen few থাকেন, তাহলে আমাদের ভগ্নোদ্যম হবার কারণ নেই।
১৩২২ কার্তিক
বস্তুতন্ত্র বস্তু কি
শ্ৰীযুক্ত রাধাকমল মুখখাপাধ্যায় রবীন্দ্রবাবুর বাস্তব’ নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তর্কই হচ্ছে আলোচনার প্রাণ। পৃথিবীর অপর সকল বিষয়ের ন্যায় সাহিত্য সম্বন্ধেও কোনো মীমাংসায় উপস্থিত হতে হলে বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই উক্তি শোনাটা দরকার।
এই উপলক্ষে রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের দোষগুণ বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তার কারণ, রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে বস্তুতন্ত্র নেই বললে, আমার বিশ্বাস, কিছুই বলা হয় না। কোন্ কাব্যে কি আছে তাই আবিষ্কার করা এবং প্রকাশ করাই হচ্ছে সমালোচনার, শুধু মুখ্য নয়, একমাত্র উদ্দেশ্য। অবিমারকে যা আছে শকুন্তলায় তা নেই, শকুন্তলায় যা আছে মৃচ্ছকটিকে তা নেই, এবং মৃচ্ছকটিকে যা আছে উত্তররামচরিতে তা নেই— এ কথা সম্পূর্ণ সত্য হলেও এ সত্যের দৌলতে আমাদের কোনোরূপ জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। কোনো-এক ব্যক্তি আইল্যাণ্ড সম্বন্ধে একখানি একছত্র-বই লেখেন। তার কথা এই যে, আইসল্যাণ্ডে সাপ নেই। এই বইখানি সম্বন্ধে ইউরোপের সকল সমালোচক একমত এবং সে মত এই যে, উক্ত পুস্তকের সাহায্যে আইল্যাণ্ড সম্বন্ধে কোনোরূপ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কোনো বিশেষ পদার্থের অভাব নয়, সদ্ভাবের উপরেই মানুষের মনে বিষয়ক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।
রবীন্দ্রবাবুর কাব্য সম্বন্ধে রাধাকমলবাবুর মতের প্রতিবাদ আমার উদ্দেশ্য নয়। কোনো-একটি মতের খণ্ডন করতে হলে সে মতটি যে কি, তা জানা আবশ্যক। আইসল্যাণ্ডে সাপ নেই— এ কথা অপ্রমাণ করবার জন্য লোককে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, সে দেশে সাপ আছে, এবং তার জন্য সাপ যে কি বস্তু সে বিষয়েও স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে বস্তুতন্ত্রতা আছে কি নেই সে বিচার করতে আমি অপারগ, কেননা
কমলবাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে বস্তুতন্ত্র যে কি বস্তু তার পরিচয় আমি লাভ করতে পারি নি। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিত্যবস্তুর উল্লেখ করেছেন। বস্তুতন্ত্রতার অর্থগ্রহণ করা যদি কঠিন হয় তাহলে নিত্যবস্তুতন্ত্রতার অর্থগ্রহণ করা যে অসম্ভব, সে কথা বলা বাহুল্য। সেই বস্তুই নিত্য, যা কালের অধীন নয়। এরূপ পদার্থ যে পৃথিবীতে আছে এ কথা এ দেশের প্রাচীন আচার্যেরা স্বীকার করেন নি। বিষ্ণুপুরাণের মতে–
যাহা কালান্তরেও অর্থাৎ কোনো কালেও পরিণামাদিজনিত সংজ্ঞার প্রাপ্ত হয় না, তাহাই প্রকৃত সত্য বস্তু। জগতে সেরূপ কোনো বস্তু আছে কি?–কিছুই নাই। (রামানুজধৃত বচন, শ্ৰীভাষ্য)
যে বস্তু জগতে নেই, সে বস্তু যদি কোনো কাব্যে না থাকে তাহলে সে কাব্যের বিশেষ কোনো দোষ দেওয়া যায় না, কেননা এই জগই হচ্ছে সাহিত্যের অবলম্বন।
২.
বস্তুতন্ত্রতা আত্মপরিচয় না দিলেও তার পরিচয় নেওয়াটা আবশ্যক; কেননা এ বাক্যটির দাবি মস্ত। বস্তুতন্ত্রতা একাধারে সকল সাহিত্যের মাপকাঠি ও শাসনদণ্ড, সুতরাং সাহিত্যসমাজে এর প্রচলন বিনা বিচারে গ্রাহ্য করা যায় না।
এ বাক্যটি বাংলা সাহিত্যে পূর্বে ছিল না। সুতরাং এই অপরিচিত আগন্তুক শব্দটির কুলশীলের সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।
এ বাক্যটি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নেই, দর্শনশাস্ত্রে আছে।
কাব্যে ও দর্শনে যোগাযোগ থাকলেও এ দুটি যে পৃথক্ জাতীয় সাহিত্য, এ সত্য তো সর্বলোকবিদিত। দার্শনিকমাত্রেই নাম-রূপের বহিভূত দুটিএকটি ধ্রুব সত্যের সন্ধানে ফেরেন; অপর পক্ষে নাম-রূপ নিয়েই কবিদের কারবার। সুতরাং দার্শনিক পরিভাষার সাহায্যে কাব্যের রূপগুণের পরিচয় দেবার চেষ্টা সকল সময়ে নিরাপদ নয়। তবে শংকরের বস্তুতন্ত্রতা কাব্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে আমার বিশেষ কোনো আপত্তি নেই। শংকরের মতে—
জ্ঞান কেবল বস্তুতন্ত্র, অর্থাৎ জ্ঞান প্রমাণ-সাপেক্ষ; প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়াই জন্মে, অতএব জ্ঞান ইচ্ছানুসারে করা না-করা এবং অন্যথা করা যায় না।
শংকর একটি উদাহরণ দিয়ে তার মত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেটি এই–
হে গোতম! পুরুষও অগ্নি, স্ত্রীও অগ্নি ইত্যাদি শ্রুতিতে যে স্ত্রী-পুরুষে বহ্নিবুদ্ধি উৎপাদন করিবার বিধান আছে, তাহা মনঃসাধ্য অর্থাৎ তাহা মনের অধীন, পুরুষের অধীন এবং শাস্ত্রীয় আজ্ঞাবাক্যেরও অধীন। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি, তাহা না পুরুষের অধীন, না শাস্ত্রীয় আজ্ঞাবাক্যের অধীন। অতএব জ্ঞান প্রত্যক্ষ-বিষয়-বস্তুতন্ত্র।
সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অর্থ যদি প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয়, তাহলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বস্তুতন্ত্রতার অভাবে দর্শন হতে পারে কিন্তু কাব্য হয় না। যদি বর্ণনার গুণে কোনো কবির হাতে বেল কুল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে যে তার বেলকুল ভুল হয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাধাকমলবাবু অবশ্য যদৃষ্টং তল্লিখিতং অর্থে ও বাক্য ব্যবহার করেন না; কেননা যে কবির হাতে বাংলার মাটি এবং বাংলার জল পরিচ্ছন্ন মূর্তি লাভ করেছে তার কাব্যে যে পূর্বোক্ত হিসেবে বস্তুতন্ত্র নেই, এ কথা কোনো সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। দেশের রূপের সম্বন্ধে যিনি দেশসুদ্ধ লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন তার যে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান নেই, এ কথা চোখের মাথা না খেয়ে বলা চলে না। শংকরের বস্তুতন্ত্রতাকে যদি কোনো বিশেষণে বিশিষ্ট করতে হয়, তাহলে সেটির অনিত্যবস্তুতন্ত্রতা সংজ্ঞা দিতে হয়। কেননা প্রসিদ্ধ অগ্নি’ ইত্যাদি যে অনিত্য বস্তু সে তো সর্বদর্শনসম্মত। সুতরাং রাধাকমলবাবুর মত এবং শংকরের মত এক নয়, কেননা নিত্যবস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে অনিত্যবস্তুতন্ত্রতার আকাশপাতাল প্রভেদ। সত্য কথা এই যে, বস্তুতন্ত্রতা নামে সংস্কৃত হলেও পদার্থটি আসলে বিলেতি। সেইজন্য রাধাকমলবাবু তার প্রবন্ধে তাঁর মতের সপক্ষে কেবলমাত্র ইউরোপীয় -লেখকদের মত উদ্ধৃত করতে বাধ্য হয়েছেন, যদিচ সেসকল লেখকদের পরস্পরের মতের কোন মিল নেই। জর্মান দার্শনিক অয়কেন এবং ইংরেজ নাটককার বার্নার্ড শ যে সাহিত্যজগতে একপন্থী নন, এ কথা তাঁদের সঙ্গে যার পরিচয় আছে তিনিই জানেন।
ইউরোপীয় সাহিত্যের রিয়ালিজমই নাম ভাঁড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র নামে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বস্তুতন্ত্রতার বিচার করতে হলে অন্ততঃ দু কথায় এই রিয়ালিজমের পরিচয় দেওয়াটা আবশ্যক।
ইউরোপের দার্শনিক-জগতেই এ শব্দটি আদিতে জন্মলাভ করে। আইডিয়ালিজমের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েই রিয়ালিজম্ দর্শনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, এবং সেই অবধি আজ পর্যন্ত এ উভয়ের যুদ্ধ সমানে চলে আসছে। আইডিয়ালিজমের মূল কথা হচ্ছে, ব্ৰহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; এবং রিয়ালিজমের মূল কথা, জগৎ সত্য ব্ৰহ্ম মিথ্যা। এ অবশ্য অতি স্কুল প্রভেদ। কেননা এ উভয় মতই নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। এবং এইসকল শাখায়-প্রশাখায় কোনো কোনো স্থলে প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে তাদের ইতরবিশেষ করা কঠিন। দর্শনের ক্ষেত্রে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয় ক্রমে তা সাহিত্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষতঃ গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সহায়তা লাভ করে রিয়ালিজম্ ইউরোপীয় সাহিত্যে একাধিপত্য লাভ করবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার আইডিয়ালিজমের উপরে প্রবল পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করে।
রাধাকমলবাবু বস্তুতন্ত্রতার সপক্ষে বার্নাড শ -র দোহাই দিয়েছেন। বার্নার্ড শ প্রমুখ লেখকদের মতে রিয়ালিজমের অর্থ যে আইডিয়ালিজমের উপর আক্রমণ, তার স্পষ্ট প্রমাণ তার নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, ইবসেনের নাটকের সারমর্ম হচ্ছে : His attacks on ideals and idealisms। এবং এই দুই মনোভাবের প্রতি বার্নার্ড শ -র যে কতদূর ভক্তি আছে তার পরিচয়ও তিনি নিজমুখেই দিয়েছেন। তিনি বলেন–
I have sometimes thought of … substituting in this book the words idol and idolatry for ideal and idealism; but it would be impossible without spoiling the actuality of Ibsen’s criticism of society. If you call a man a rascally idealist, he is not only shocked and indignant but puzzled : in which condition you can rely on his attention. If you call him a rascally idolater, he concludes calmly that you do not know that he is a member of the Church of England. I have therefore left the old wording. (The Quintessence of Ibsenism)
বার্নাড শ -র অভিমত-বস্তুতন্ত্রতা রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে সম্ভবতঃ নেই। কিন্তু রাধাকমলবাবু কখনোই বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় বস্তুতন্ত্রতার চর্চা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কেননা তিনি চান যে, সাহিত্য জনসাধারণের মনে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করবে; অপর পক্ষে বার্নার্ড শ চান যে, সাহিত্য জনসাধারণের মন থেকে তথাকথিত উচ্চ আদর্শসকল দূর করবে।
রিয়ালিজম্ শব্দটি কিন্তু একটি বিশেষ সংকীর্ণ অর্থেই ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপরিচিত। এক কথায় রিয়ালিস্টিক সাহিত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা, এবং ভিক্টর হুগো প্রমুখ লেখকদের রচিত সাহিত্যের প্রতিবাদ স্বরূপেই ফ্লবেয়ার প্রমুখ লেখকেরা এই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।
রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ এই যে, সে সাহিত্য মনগড়া সাহিত্য। রোমান্টিক কবিদের মানস পুত্র ও মানসী কন্যারা এ পৃথিবীর সন্তান নন এবং যে জগতে তারা বিচরণ করেন সেটি কবিদের স্বকপোলকল্পিত জগৎ। এক কথায় সে রূপের রাজ্যটি রূপকথার রাজ্য। উক্ত শ্রেণীর কবিরা নিজের কুক্ষিস্থ উপাদান নিয়ে যে মাকড়সার জাল বুনেছিলেন ফরাসি রিয়ালিজম্ তারই বক্ষে নখাঘাত করে। এ অভিযোগের মূলে যে অনেকটা সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এক গীতিকাব্য বাদ দিলে ফরাসিদেশের গত শতাব্দীর রোমান্টিক লেখকদের বহু নাটক-নভেল যে অশরীরী এবং প্রাণহীন, সে কথা সত্য। কিন্তু একমাত্র সুন্দরের চর্চা করতে গিয়ে সত্যের জ্ঞান হারানো যেমন রোমান্টিকদের দোষ, সত্যের চর্চা করতে গিয়ে সুন্দরের জ্ঞান হারানোটাও রিয়ালিস্টদের তেমনি দোষ; প্রমাণ, জোলা Zola। আকাশগঙ্গা অবশ্য কাল্পনিক পদার্থ। কিন্তু তাই বলে কাব্যে মন্দাকিনীর পরিবর্তে খোলা নর্দমাকে প্রবাহিত করার অর্থ তার জীবনদান করা নয়। রাধাকমলবাবু অবশ্য এ জাতীয় রিয়ালিজমের পক্ষপাতী নন। কেননা তার মতে যেটি এ দেশের আদর্শ কাব্য অর্থাৎ রামায়ণ, সেটি হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান রোমান্স। জোলা প্রভৃতি রিয়ালিজমের দলবল সরস্বতীকে আকাশপুরী হতে শুধু নামিয়েই সন্তুষ্ট হন নি, তাকে জোর করে মর্তের ব্যাধিমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। কারণ রোগ যে বাস্তব, সে কথা আমরা চীৎকার করে মানতে বাধ্য।
৩.
রাধাকমলবাবু যখন দেশি কাব্যের গায়ে বিলাতি ফুলের গন্ধ থাকাতেই আপত্তি করেন, তখন অবশ্য তিনি আমাদের সাহিত্যে বিলাতি ওষুধের গন্ধ আমদানি করতে চান না। তিনি বস্তুতন্ত্রতা অর্থে কি বোঝেন, তা তার প্রদত্ত দুটি-একটি উপমার সাহায্যে আমরা কতকটা আন্দাজ করতে পারি। রাধাকমলবাবু বলেন
মৃণাল না থাকিলে লতিকা না থাকিলে পদ্ম যে ঢলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য কি করিয়া ফুটিয়া উঠিবে?
জীবন্ত গাছ হইতেছে সাহিত্যের আসল বাস্তব। সে গাছ তাঁহার শিকড়ের দ্বারা জাতির অন্তরতম হৃদয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছে, সমস্ত জাতির হৃদয় হইতে তাঁহার রসসঞ্চার হয়। এই রসসঞ্চারই সাহিত্যে বাস্তবতার লক্ষণ।
একটা গোলাপগাছের যদি আশা হয়, সে স্থান কাল ও অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নীচের মাটি হইতে রস সঞ্চয় না করিয়া, আলোক ও বাতাসের দানকে অবজ্ঞা করিয়া, এক কথায় বাস্তবকে না মানিয়া, সে লিলি ফুল ফুটাইবে তাহা হইলে তাঁহার যেরূপ বিড়ম্বনা হয়, কোনো দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টাও সেইরূপ ব্যর্থ হয়।
এর অনেক কথাই যে সত্য, সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। মৃণালের অস্তিত্ব না থাকলে পদ্মের ঢলে পড়ার চাইতেও বেশি দুরবস্থা ঘটবে, অর্থাৎ তার। অস্তিত্বই থাকবে না। তবে মৃণাল যদি বাস্তব হয়, পদ্ম যে কেন তা নয়, তা বোঝা গেল না। সম্ভবতঃ তার মতে যে যার নীচে থাকে সেই তার বাস্তব। ফুলের তুলনায় তার বৃন্ত, বৃন্তের তুলনায় শাখা, শাখার তুলনায় কাণ্ড, কাণ্ডের। তুলনায় শিকড় এবং শিকড়ের তুলনায় মাটি উত্তরোত্তর অধিক হতে অধিকতর এবং অধিকতম বাস্তব হয়ে ওঠে। পঙ্কজের অপেক্ষা পঙ্কে যে অধিক পরিমাণে বাস্তবতা আছে, এই বিশ্বাসে জোলা প্রভৃতি বস্তুতান্ত্রিকেরা মানবমনের এবং মানবসমাজের পঙ্কোদ্ধার করে সরস্বতীর মন্দিরে জড়ো করেছিলেন। রাধাকমলবাবু কি চান যে আমরাও তাই করি? গোলাপগাছের পক্ষে লিলি প্রসব করবার প্রয়াসটি যে একেবারেই ব্যর্থ শুধু তাই নয়, মাটি হতে রস সঞ্চয় না করে আলোক ও বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করে সে গোলাপও ফোঁটাতে পারবে না, কেননা ওরূপ ব্যবহার করলে গোলাপগাছ দুদিনেই দেহত্যাগ করতে বাধ্য হবে।
গাছের ফুল আকাশে ফোটে কিন্তু তার মূল যে মাটিতে আবদ্ধ, সে কথা আমরা সকলেই জানি; সুতরাং কবিতার ফুল ফুটলেই আমরা ধরে নিতে পারি যে মনজগতে কোথাও-না-কোথাও তার মূল আছে। কিন্তু সে মূল ব্যক্তিবিশেষের মনে নিহিত নয়, সমাজের মনে নিহিত, এই হচ্ছে নূতন মত। এ মত গ্রাহ্য করবার প্রধান অন্তরায় এই যে, সামাজিক মন বলে কোনো বস্তু নেই; ও পদার্থ হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাবস্ট্রাকশন।
সে যাই হোক, রাধাকমলবাবু এই সহজ সত্যটি উপেক্ষা করেছেন যে, গোলাপের গাছে অবশ্য লিলি ফোটে না কিন্তু একই ক্ষেত্রে গোলাপও জন্মে লিলিও জন্মে। স্বদেশের ক্ষেত্রেও যে বিদেশি ফুলের আবাদ করা যায়, তার প্রমাণ স্বয়ং গোলাপ। পারশ্যদেশের ফুল আজ ভারতবর্ষের ফুলের রাজ্যে গৌরব এবং সৌরভের সহিত নবাবি করছে।
বহির্জগতে যদি এক ক্ষেত্রে নানা ফুল ফোটে, তাহলে মনোজগতের যে-কোনো ক্ষেত্রে অসংখ্য বিভিন্নজাতীয় ফুল ফোটবার কথা। কেননা, খুব সম্ভব, মনোজগতের ভূগোল আমাদের পরিচিত ভূগোলের অনুরূপ নয়। সে জগতে দেশভেদ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে অন্ততঃ অলঙ্ঘ্য পাহাড়পর্বতের ব্যবধান নেই, এবং মানুষের হাতে গড়া সে রাজ্যের সীমান্ত-দুর্গসকল এ যুগে নিত্য ভেঙে পড়ছে। ভাবের বীজ হাওয়ায় ওড়ে এবং সকল দেশেই অনুকূল মনের ভিতর সমান অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে লিলি ফুটলে আঁতকে ওঠবার কোনো কারণ নেই। রাধাকমলবাবু বলেছেন–
জাতীয় মনের ক্ষেত্র হইতেই কবির মন রস সঞ্চয় করে।
যদি এ কথা সত্য হয় তাহলে যদি কোনো কাব্য শুষ্ক কাষ্ঠ মাত্র হয় তাহলে তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী হচ্ছে সামাজিক মন। জাতীয় মন যদি নীরস হয় তাহলে কাব্য কোথা হতে রস সঞ্চয় করবে। উপমান্তরে দেশমাতার স্তনে যদি দুগ্ধ না থাকে তাহলে তার কবিপুত্রকে যে পেঁচোয় পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি।
কিন্তু রাধাকমলবাবুর এ মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। কবির মনের সঙ্গে জাতীয় মনের যোগাযোগ থাকলেও কবিপ্রতিভা সামাজিক মনের সম্পূর্ণ অধীন নয়।
রাধাকমলবাবু উদ্ভিজগৎ হতে যে উপমা দিয়েছেন, ইউরোপে ঘোর মেটিরিয়ালিজমের যুগে ঐ উপমাটি জড়জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে যোগসাধনের সেতুস্বরূপ ব্যবহৃত হত। মাটি জল আলো ও বাতাস প্রভৃতির যোগাযোগে জীব সৃষ্ট হয়েছে এবং জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তার মনের সৃষ্টি হয়েছে, এই বিশ্বাসবশতঃই ইউরোপের একদল বস্তুতান্ত্রিক-দার্শনিক ধর্ম কাব্য আর্ট নীতি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাপারসকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ওরূপ ব্যাখ্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থারই বর্ণনা করা হয়েছিল, কাব্য প্রভৃতির বিশেষ-ধর্মের কোনো পরিচয় দেওয়া হয় নি। দার্শনিক ভাষায় বলতে গেলে, তারা কাব্যের উপাদান-কারণকে তার নিমিত্ত-কারণ বলে ভুল করেন। তাঁরা বাহ্যশক্তিতে বিশ্বাস করতেন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করতেন না; সুতরাং তাদের মতে কবির আত্মশক্তি নয়, পারিপার্শ্বিক সমাজের বাহ্যশক্তিই কাব্যের উৎপত্তির কারণ বলে স্থিরীকৃত হয়েছিল। কবিতার জন্ম ও কবির জন্মবৃত্তান্ত
যে স্বতন্ত্র, এই সত্য উপেক্ষা করবার দরুন সাহিত্যতত্ত্ব সমাজতন্ত্রের অন্তত হয়ে পড়েছিল।
রাধাকমলবাবুর বস্তুতন্ত্রতা ইউরোপের গত শতাব্দীর মেটিরিয়ালিজমের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বই আর কিছু নয়।
আসল কথা এই যে, প্রতি কবির মন এক-একটি স্বতন্ত্র রসের উৎস। কবির কার্য হচ্ছে সামাজিক মনকে সরস করা। কবির মনের সঙ্গে অবশ্য সামাজিক মনের আদানপ্রদানের সম্পর্ক আছে। কবি কিন্তু সমাজের নিকট হতে যা গ্রহণ করেন সমাজকে তার চাইতে ঢের বেশি দান করেন। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কবি এই অতিরিক্ত রস কোথা হতে সংগ্রহ করেন? তার উত্তরে আমরা বলব, আধ্যাত্মিক জগৎ হতে; সে জগৎ অবাস্তবও নয় এবং তা কোনো পরম ব্যোমেতেও অবস্থিতি করে না। সে জগৎ আমাদের সত্তার মূলে ও ফুলে সমান বিদ্যমান। কারণ আত্মা হচ্ছে সেই বস্তু–
শ্রোত্রস্য শ্ৰোত্ৰং মনসো মনো য বাচো হ বাচম্।
স উ প্রাণস্য প্রাণঃ…।।
রামানুজ বলেন, আমরা বদ্ধমুক্ত জীব। আমাদের মন যে অংশে এবং যে পরিমাণে বহির্জগতের অধীন, সেই অংশে এবং সেই পরিমাণে তা বদ্ধ; এবং যে অংশে ও যে পরিমাণে তা স্বাধীন সে অংশে ও সে পরিমাণে তা মুক্ত। আমরা যখন বহির্জগতের সত্যসুন্দরমঙ্গলের কেবলমাত্র দ্রষ্টা, তখন আমরা বদ্ধ জীব; এবং আমরা যখন নূতন সত্যসুন্দরমঙ্গলের স্রষ্টা, তখন আমরা মুক্ত জীব। যার স্বাধীনতা নেই তাঁর সাহিত্যে কোনো কিছুরই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই। তিনি বড়জোর বিশ্বের রিপোর্টার হতে পারেন, তার বেশি নয়। ধর্মপ্রবর্তক কবি আর্টিস্ট প্রভৃতিই মানবের যথার্থ শিক্ষক, কেননা তারাই মানবসমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। এই কারণে যিনি যথার্থ কবি তিনি সমাজের ফরমায়েশ খাটতে পারেন না, তার জন্য যদি তাকে আত্মম্ভরি বল তাতে তিনি আত্মনির্ভরতা ত্যাগ করবেন না। যে দেশে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করাই সাধনার চরম লক্ষ্য বলে গণ্য, সে দেশে কবিকে আত্মতান্ত্রিক বলে নিন্দা করা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।
৪.
দেশকালের ভিতর সম্পূর্ণ বদ্ধ না করতে পারলে অবশ্য জড়বস্তুর সঙ্গে মানবমনের ঐক্য প্রমাণ করা যায় না। মেটিরিয়ালিজমের পাকা ভিতের উপর খাড়া না করলে রিয়ালিজমের গোঁড়ায় গলদ থেকে যায়। অতএব রাধাকমলবাবু কবিপ্রতিভাকে কেবলমাত্র স্বদেশ নয়, স্বকালেরও সম্পূর্ণ অধীন করতে চান। তিনি বলেন–
সাহিত্যের চরম সাধনা হইয়াছে যুগধর্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা। যদি তাই সত্য হয়, তাহলে মহাভারতাদি ব্যতীত অপর কোনো কাব্য স্বদেশি এবং জাতীয় নয়, এ কথা বলবার সার্থকতা কি। ও-জাতীয় কাব্য আমরা রচনা করতে পারি নে, কেননা আমরা ত্রেতা কিংবা দ্বাপর যুগের লোক নই। ন্যাশনাল এপিক রচনা করা এ যুগে অসম্ভব, কেননা ওসকল মহাকাব্যকে অপৌরুষেয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ সাহিত্য কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নি। যুগে যুগে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েই ভারতী-কথা মহাভারতে পরিণত হয়েছে। যুগধর্ম যাই হোক, কোনো অতীত যুগের পুনরাবৃত্তি করা কোনো যুগেরই ধর্ম নয়।
যদি যুগধর্ম অনুসরণ করতে হয়, তাহলে এ যুগে কবিদের পক্ষে বিদেশি এবং বিজাতীয় ভাববর্জিত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব, কেননা আমরা বাংলার। মাটিতে বাস করলেও বিলাতের আবহাওয়ায় বাস করি। আমাদের মনের নবদ্বার দিয়ে ইউরোপীয় মনোভাব অহর্নিশি আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করছে। কাজেই যুগধর্ম অনুসারে আমরা আমাদের সাহিত্যে একটি নব এবং মিশ্র মনোভাব প্রকাশ করে থাকি। আমাদের সাহিত্যের গুণও এই, দোষও এই।
এ সাহিত্যের গুণাগুণ এই দেশি-বিলাতি মনোভাবের যথাযথ মিলনের উপর নির্ভর করে। দু ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে একভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত হলে জলের সৃষ্টি হয়, যা পান করে মানবের পিপাসা নিবারণ হয়। অপর পক্ষে দু ভাগ অক্সিজেনের সঙ্গে এক ভাগ হাইড্রোজেন মিশ্রিত হলে যে বাষ্পের সৃষ্টি হয়, তা নাকে-মুখে ঢুকলে হয়তো আমরা দম আটকে মারা যাই। শুধু তাই নয়, মাত্রা ঠিক থাকলেও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে মিলে জল হয় না, যদি না তাদের উভয়ের রাসায়নিক যোগ হয় অর্থাৎ যদি না ও-দুটি ধাতু পরস্পর পরস্পরের ভিতর সম্পূর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হয়।
এই রাসায়নিক যোগসাধনের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য চাই। সুতরাং এই দেশি-বিলাতি ভাবের মিশ্রণে এ যুগের সাহিত্যে অমৃত ও বিষ দুইই রচিত হচ্ছে। যে মনের ভিতর আত্মার বৈদ্যুতিক তেজ আছে, সে মনে এ যুগের রাসায়নিক যোেগ হয়; এবং যে মনে সে তেজ নেই, সেখানে এ দুই শুধু মিশে যায়, মিলে যায় না।
যুগধর্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম সাধনা, এ কথা সত্য নয়। তার, কারণ প্রথমত যুগধর্ম বলে কোনো যুগের একটিমাত্র বিশেষ ধর্ম নেই। একই যুগে নানা পরস্পরবিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, মনপদার্থ টি কোনো বিশেষ কাল সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক অংশে কালের অধীন, অপর অংশে মুক্ত ও স্বাধীন। কাব্য ধর্ম আর্ট প্রভৃতি মুক্ত আত্মারই লীল। সুতরাং(ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, প্রতি যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সমসাময়িক যুগধর্ম পরীক্ষিত এবং বিচারিত হয়েছে।
নব যুগধর্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয়, তাহলে সাহিত্য বর্তমান যুগধর্ম অতিক্রম করতে বাধ্য। যে আদর্শ সমাজে নেই, সে আদর্শের সাক্ষাৎ শুধু মনশ্চক্ষুতে পাওয়া যায় এবং জীবনে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজের দখলিস্বত্ববিশিষ্ট আদর্শের উচ্ছেদ করা দরকার, অর্থাৎ যুগধর্মের বিরোধী হওয়া আবশ্যক।
বার্নার্ড শ অবজ্ঞার সহিত বলেছেন যে তিনি ‘art for art’এর দলের নন। তার কারণ, তিনি এবং তার গুরু ইবসেন ইউরোপে সভ্যতার নবযুগ আনয়ন করাই জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এদের রচিত নাটকাদি যে সাহিত্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সে যে কতটা তাদের মতের গুণে এবং কতটা তাদের আর্টের গুণে, তা আজকের দিনে বলা কঠিন। কেননা, তারা যে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করতে উদ্যত হয়েছেন, তার সঙ্গে সকলেরই সামাজিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। এ কথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, এ শ্রেণীর সাহিত্যে শক্তির অনুরূপ শ্ৰী নেই। সাহিত্যকে কোনোএকটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ করে তুললে তাকে সংকীর্ণ করে ফেলা অনিবার্য। আমরা সামাজিক জীব, অতএব নূতন-পুরাতনের যুদ্ধেতে একপক্ষে-না-একপক্ষে আমাদের যোগ দিতেই হবে, কিন্তু আমাদের সমগ্র মনটিকে যদি আমরা এই যুদ্ধে নিয়োজিত করি তাহলে আমরা সনাতনের জ্ঞান হারাই। যা কোনো-একটি বিশেষ যুগের নয়, কিন্তু সকল যুগেরই হয় সত্য নয় সমস্যা, তাই হচ্ছে মানবমনের পক্ষে চিরপুরাতন ও চিরনূতন, এক কথায় সনাতন। এই সনাতনকে যদি রাধাকমলবাবু নিত্যবস্তু বলেন, তাহলে সাহিত্যের যে নিত্যবস্তু আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না; কিন্তু ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিকেরা তা অগ্রাহ্য করবেন। একান্ত বিষয়গত সাহিত্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার ইচ্ছা থেকেই ‘art for art’ মতের উৎপত্তি হয়েছে। (কাব্য বল, ধর্ম বল, দর্শন বল, এসকল হচ্ছে বিষয়ে নিলিপ্ত মনের ধর্ম। এই সত্য উপেক্ষা করার দরুন ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। রাধাকমলবাবু প্রমুখ লেখকদের বস্তুতান্ত্রিকতা যে ইউরোপের রিয়ালিজম্ ব্যতীত আর কিছুই নয়, তার প্রমাণস্বরূপ অয়কেন-বর্ণিত উক্ত মতের লক্ষণগুলি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। উক্ত জর্মান দার্শনিকদের মত শিরোধার্য করতে রাধাকমলবাবুই যখন আমাদের আদেশ করেছেন, তখন সে মত অবশ্য তাঁর নিকট গ্রাহ্য হবে। অয়কেন বলেন যে, রিয়ালিজম্ প্রকৃতিকেই সব বলে ধরে নেয় এবং যে বস্তুর বহির্জগতে অস্তিত্ব আছে তাই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব।
এ দলের অধিকাংশ লোক, যা ইন্দ্রিয়গোচর তাই সত্য বলে গ্রাহ্য করেন এবং জনকতক আছেন, যাদের মতে বিশ্ব একটি যন্ত্র মাত্র এবং যেহেতু মাপজোখের সাহায্য ব্যতীত যন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং যে বস্তুকে মাপা যায় এবং ওজন করা যায় তাই হচ্ছে বাস্তব।
অর্থাৎ যা আঁকা যায় এবং যার আঁক-কষা যায় তাই একমাত্র সত্য। তার পর এ মতে–
ভাবরাজ্যে কোনোরূপ আইডিয়ালের অস্তিত্ব ভ্রান্তি মাত্র, কিন্তু নীতির রাজ্যে আইডিয়াল (আদর্শ) আছে এবং থাকা উচিত। কেননা এ মতে জ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সমাজ বহু ব্যক্তিকে জোড়া দিয়ে তৈরি একটি যন্ত্র মাত্র; আবার কর্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তা একটি অর্গানিজম্ (অঙ্গী) এবং প্রতি ব্যক্তি তার অঙ্গ, অতএব ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের সম্পূর্ণ অধীন। স্বাধীনতা বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব বিশ্বেও নেই, মানবের অন্তরেও নেই। অথচ এ মতে রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতাসাধনাই হচ্ছে পরম ধর্ম।
মানবসমাজকে হয় যন্ত্র নয় অঙ্গী স্বরূপে গ্রাহ্য করলে এবং মানবের আত্মার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করলে এই যন্ত্রের অংশ অথবা এই অঙ্গীর অঙ্গ যে-ব্যক্তি তার অপর সকল ধর্মকর্মের ন্যায় তার সাহিত্যরচনাও সম্পূর্ণ সমাজের অধীন, এবং সমাজ যখন অঙ্গী তখন তা অবশ্য সম্পূর্ণ যুগধর্মের অধীন এবং তার প্রতি অঙ্গও সেই একই যুগধর্মের অধীন। সুতরাং কোনো ব্যক্তির পক্ষে মনজগতে যুগধর্ম অতিক্রম করবার চেষ্টা শুধু ধৃষ্টতা নয়, একেবারেই বাতুলতা। আমাদের দেশে যারা বস্তুতন্ত্রতার ধুয়ো ধরেছেন, তারা যে ইউরোপের এই জাতীয় রিয়ালিজমের চর্বিতচর্বণ রোমন্থন করেছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমি অয়কেনের আর-একটি কথা উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি—
All spiritual creation possesses a superiority as compared with the age and liberates man from its compulsion, nay, it wages an unceasing strtiggle against all that belongs to the things of mere time.
যথার্থ কবির নিকট এ সত্য প্রত্যক্ষ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের চোখরাঙানি হেলায় উপেক্ষা করতে পারেন।
৫.
আসল কথা, এসকল ন্যায়ের তর্কের সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা নেই। অহীন বস্তু কিংবা পদার্থহীন ভাব, এ দুয়ের কোনোটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। রিয়ালিজমের পুতুলনাচ এবং আইডিয়ালিজমের ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে, সে কারণ যা হয় বস্তুহীন নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একাধারে রিয়ালিস্ট এবং আইডিয়ালিস্ট; কি বহির্জগৎ কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তা ছাড়া কবির দৃষ্টি সাধারণ জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে।
The light that never was on_land or sea, সেই আলোকে বিশ্বদর্শন করবার শক্তিকেই আমরা কবিপ্রতিভা বলি, কেননা সে জ্যোতি বাহজগতে নেই, অন্তর্জগতেই তা আবিভূত হয়।
রিয়ালিজমের এই উচ্চবাচ্য ইউরোপীয় সাহিত্যেই যখন বিরক্তিজনক, তখন বাংলা সাহিত্যে তা একেবারেই অসহ। ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে বস্তুজগতের উপর প্রভুত্ব করছে, অপর পক্ষে বৈজ্ঞানিক-দর্শন আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানের যে অংশটি খাঁটি সেইটি ইউরোপের হাতে পড়েছে, এবং তার যে অংশটি ভুয়ো, সেইটিই আমাদের মনে ধরেছে। ইউরোপ পঞ্চভূতকে তার দাসত্বে নিযুক্ত করেছে, আর আমরা তাদের পঞ্চদেবতা করে তোলবার চেষ্টায় আছি।
১৩২১ মাঘ
বাংলার ভবিষ্যৎ
মির্জাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরিতে পঠিত
বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন তখন তিনি বাঙালির পক্ষে বাংলা লেখার ঔচিত্য এবং সার্থকতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে বাধ্য হন। বঙ্গদর্শনের ‘পত্র সূচনা’ বঙ্গসরস্বতীর তরফ থেকে একাধারে আরজি, জবাবু ও সওয়ালজবাব। বাংলা লেখার জন্য বাঙালির পক্ষে স্বদেশি শিক্ষিতসমাজের নিকট কোনোরূপ কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন যে একদিন ছিল, এ ব্যাপার আজকের দিনে আমাদের কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকে—
যতদিন না শিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙালিরা বাংলা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙালির উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নাই…
বঙ্কিমের এ উক্তির সত্যতা যে যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে, এ আমাদের ধারণার বহিভূত। কেননা এ সত্য আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে না উঠলেও স্বীকার্য হয়েছে; কিন্তু বঙ্কিম যে সময়ে লেখনীধারণ করেন, সে সময়ে এ সত্যকে মেনে নেওয়া দূরে থাক, কেউ ধরে নিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। সে যুগে ছিল ইংরেজির রেওয়াজ এবং ইংরেজিরই প্রতিপত্তি। সেকালের শিক্ষিতসম্প্রদায়, অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়, ইংরেজি লিখতেন, ইংরেজি ছাড়া আর কিছু লিখতেনও না, এবং সম্ভবতঃ কথাবার্তাও কইতেন ঐ রাজভাষাতেই। নতুবা বঙ্কিমের এ কথা বলবার কোনো আবশ্যকতা ছিল না যে ইংরেজি লেখক, ইংরেজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরেজ ভিন্ন কখনো খাঁটি বাঙ্গালির সমুভবের সম্ভাবনা নাই।
২.
এ খুব বেশি দিনের কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এ লেখার তারিখ হচ্ছে পয়লা বৈশাখ, ১২৭৯ সাল। জাতীয় জীবনের হিসাবে পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতি স্বল্প কাল, কিন্তু এই স্বল্প কালের মধ্যেই বাংলার শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনে মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ভাবান্তর ঘটেছে, বাংলা ভাষার প্রতি অভক্তি স্পষ্টতঃ অতিভক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের মধ্যে বাংলা লেখার প্রবৃত্তি বর্তমানে যে কতটা অদম্য হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় আমাদের মাসিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। যে দেশে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে একখানি মাসিক পত্র বার করতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ লেখকেরও জবাবদিহি ছিল, সেই দেশে আজকের দিনে নিত্য নূতন মাসিক পত্রের জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে, অথচ তার জন্য আমাদের। সাধারণ লেখকদেরও কারও কাছে কোনোরূপ কৈফিয়ত দিতে হয় না। এই কলিকাতা শহর থেকে মাসে মাসে কত কাগজের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তারই সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য, কেননা এ ক্ষেত্রে জন্মমৃত্যুর কোনো সঠিক রেজেস্টারি রাখা হয় না। যদিচ এখন কাগজের আকাল পড়েছে, তথাপি বাজারে নূতন কাগজের কোনো অভাব নেই। তার পর বাংলার পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের নানা নগরী ও উপনগরী থেকে নানা আকারের নানা বর্ণের নানা পত্র পরস্পর রেষারেষি করে শূন্যমার্গে উডীন হয়ে সাহিত্যগগনের শোভা বৃদ্ধি করছে। বঙ্গসরস্বতীকে ঢাকা দান করেছে প্রতিভা, মৈমনসিং ‘সৌরভ’, বহরমপুর ‘উপাসনা’, এবং কুচবেহার ‘পরিচারিকা। এক কথায়, এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলেই দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, নব-বঙ্গসাহিত্য বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করে অঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশেও স্বীয় প্রসার লাভ ও প্রভাব বিস্তার করছে। তা ছাড়া এমন কথাও শুনতে পাই যে, গুজরাটি মারাঠি হিন্দি প্রভৃতি হাল সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে বাংলা বইয়ের ভাষায় অনুবাদ।
৩.
এক হিসেবে এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা, কেননা এ যুগে এ দেশে ইংরেজির চর্চা কমা দূরে থাক্, এতটা বেড়ে গিয়েছে যে, ইংরেজি ভাষাকে এখন বাঙালির দ্বি-মাতৃভাষা বলা যেতে পারে, যদি না বৈয়াকরণিকেরা মাতৃ-শব্দের ঐরূপ দ্বিত্বে আপত্তি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি হাতে গোনা যেত, আর আজকের দিনে তাদের সংখ্যার সন্ধান নিতে হলে সরকারবাহাদুরের আদমসুমারির খাতার অনেক পাতা ওলটাতে হয়। সেকালের শিক্ষিতসম্প্রদায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যাকে বলে ইংরেজি-বাচক, তাই ছিলেন কি না জানি নে, কিন্তু এ কথা আমরা সবাই জানি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশে এক নবসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, যে সম্প্রদায় বাংলা কথা ভুলেও মুখে আনতেন না, এমনকি ঘরেও নয়। সেই ইঙ্গবঙ্গ-সম্প্রদায়ের লোকেরাও যে আজ বাংলা বলেন, বাংলা লেখেন, এমনকি প্রকাশ্য সভাসমিতিতে খাঁটি বাংলায় বক্তৃতা পর্যন্ত করতে পিছপা হন না, তার পরিচয় লাভ করবার জন্য আপনাদের অন্যত্র যেতে হবে না। আমার এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে উপস্থিত শ্ৰোতৃমণ্ডলীর চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘটবার কোনোই সম্ভাবনা নেই।
বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে এসব অবশ্য খুবই শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের দেহপুষ্টির এইসব প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখে যদি কেউ মনে করেন যে, ‘বাংলা বনাম ইংরেজি’ এই ভাষার মামলায় বাদীর পক্ষে পুরোপুরি জয়লাভ হয়েছে, তাহলে তিনি নিতান্তই ভুল করবেন; যা হয়েছে তা হচ্ছে তরমিম ডিক্রি। ওদিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের আইন-আদালত স্কুল-কলেজ রাজদরবার-রাজনীতি জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই অদ্যাবধি ইংরেজির পুরো দখলে রয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বেশির ভাগ গণ্যমান্য লোকেরা এসকল ক্ষেত্রে ইংরেজির দখল বজায় রাখাই সংগত ও কর্তব্য মনে করেন। মাতৃভাষা ইংরেজির হাত থেকে সেইটুকু মাত্র ছাড়া পেয়েছে, যেটুকু তার পক্ষে কেঁদে বাঁচবার জন্য দরকার।
এইই যথেষ্ট প্রমাণ যে, বঙ্গসাহিত্যের যে বড়দিন এসেছে, সে দিনে বাংলা ভাষা শিক্ষিতসমাজে অবজ্ঞার পাত্র না হলেও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠে নি। পূর্বে মাতৃভাষাকে শিক্ষিতসম্প্রদায় যে যথেষ্ট অবজ্ঞা করতেন, তার প্রমাণ, তারা অনেকেই বাংলা লিখতেন না; আর আজ যে সেই সম্প্রদায় সে ভাষাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন না, তার প্রমাণ, তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলা লেখেন। প্রবৃত্তিরেষা নরাণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা’ এ শাস্ত্রবচন যে লেখা সম্বন্ধেও খাটে, এ জ্ঞান সকলের থাকলে অনেকে বঙ্গসাহিত্য রচনা করতে প্রবৃত্ত হতেন না। আমি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এঁদের অনেকের গান ও গল্প পড়ে আমার মনে হয়, বাংলা লেখাটা এদের পক্ষে একটা শখ মাত্র, অবসরবিনোদনের একটি বিশিষ্ট উপায়, ভাষায় যাকে বলে বিশুদ্ধ আমোদ। কিন্তু সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, যা অবকাশরঞ্জিনী তা কাব্য নয়, এবং যা অবসর চিন্তা তা দর্শন নয়। ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান না করলে সাহিত্যের যথার্থ চর্চা করা হয় না। লক্ষ্মীর সেবার অবসরে সরস্বতী সেবা করা যে কর্তব্য, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই, তবে প্রশ্ন হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিটি কি। আমার মতে বেশির ভাগ কাজের লোকেরা নিজে না লিখে পরের লেখা পড়েই ছুটির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে পারেন। জ্ঞানকর্মের বিভাগটা উপেক্ষা করলে কি জ্ঞান কি কর্ম কিছুরই গুণবৃদ্ধি হয় না। মানুষে সাহিত্যে যে ভাবের-ঘর বাঁধে সে খেলার-ঘর নয়, মনের বাসগৃহ। তাসের ঘর কিন্ডারগার্টেনেই শোভা পায়, সাবালক সমাজে নয়। সুতরাং যারা মাতৃভাষার যথার্থ ভক্ত, তাদের পক্ষে সে ভাষাকে সাহিত্যের রাজপাটে বসাবার জন্য এখনো বহুদিন ধরে বহু চিন্তা বহু চেষ্টা করতে হবে। বঙ্গসরস্বতীর চরণে পুস্পাঞ্জলি দেওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ নয়; তাতে ভক্তির পরিচয় দেওয়া হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানকর্মের হয় না। অতএব জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বত্বস্বামিত্ব সাব্যস্ত করবার জন্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমাদের পদে পদে তর্ক করতে হবে, বিচার করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে বিবাদ-বিসংবাদ করতেও প্রস্তুত হতে হবে। এক কথায় বঙ্গসরস্বতীর সেবককে তার সৈনিকও হতে হবে।
৪.
বিদেশি সাহিত্যের ঐশ্বর্যের তুলনায় আমাদের স্বদেশি সাহিত্যের দারিদ্র্যের পরিচয় লাভ করে হতাশ হবার অবশ্য কোনোই কারণ নেই। লোকভাষা যে কোনো দেশেই রাতারাতি স্বরা হয়ে ওঠে নি, তার প্রমাণ বর্তমান ইউরোপের সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। অপর ভাষা অপর সাহিত্যের অধীনতাপাশ থেকে ইউরোপের কোনো নবভাষাই এক দিনে মুক্তি লাভ করতে পারে নি। সাহিত্যে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার পূর্বে ইউরোপের অনেক দেশেই দেশি ভাষাকে পর পর তিনটি বাধাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। মোটামুটি ধরতে গেলে, লোকভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই : প্রথমতঃ কোনো মৃতভাষার, দ্বিতীয়তঃ কোনো বিদেশি ভাষার, এবং তৃতীয়তঃ কোনো কৃত্রিম ভাষার চাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়া।
প্রায় হাজার বৎসর কাল ল্যাটিন যে ইউরোপের সাহিত্যের ভাষা ছিল, এ সত্য অবশ্য আপনাদের সকলের নিকটই সুবিদিত। এই দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান দর্শন ধর্মশাস্ত্র ব্যবহারশাস্ত্র ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়সকল একমাত্র ল্যাটিন ভাষাতেই লিখিত হত। অপণ্ডিত লোকে অবশ্য ইউরোপের এই মধ্যযুগেও কথা ও কাহিনী, ছড়া ও পাঁচালি প্রভৃতি নিজ নিজ ভাষাতেই রচনা করত, কিন্তু সেই লোকসাহিত্য শিক্ষিতসমাজে সেকালে সাহিত্য বলে গণ্য হয় নি, সুতরাং সে সাহিত্য সেকালে যে কোনোরূপ পদমর্যাদা লাভ করে নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই ল্যাটিনের হাত থেকে ইউরোপীয় সাহিত্য যে বেশি দিন মুক্তিলাভ করে নি তার প্রমাণ, বেকন তাঁর নোম অর্গানাম, স্পিনোজা তাঁর এথিক্স, এমনকি নিউটন তার প্রিন্সিপিয়া ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। ইউরোপের কোনো কোনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন ভাষায় থিসিস লেখবার পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, বর্তমান যুগের। দিগবিজয়ী দার্শনিক বের্গ তাঁর প্রথম গ্রন্থ আদিতে ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। এ ব্যাপার যথার্থ ই বিস্ময়কর, কেননা ইউরোপের দার্শনিকসমাজে লিপিচাতুর্যে বের্গসঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই; তার হাতের কলম যথার্থ ই সোনার কাঠি, যার স্পর্শে মনোজগতের শুষ্কতরুও পত্রেপুষ্পে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, দর্শনও কাব্য হয়ে ওঠে। লোকভাষার উপর মৃতভাষার প্রভাব ও প্রভুত্ব যে কতটা দুরপনেয়, তারই প্রমাণস্বরূপ এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম। জমান। দেশে আজও এমন-সব পণ্ডিত আছেন, যাদের পাণ্ডিত্য ল্যাটিন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু তার কারণ স্বতন্ত্র। শুনতে পাই, সে জাতির কোনো কোনো পণ্ডিত স্বভাষায় লিখলে সে লেখা এত জড়ানো হয় যে, তাঁরা নিজেই তা পড়তে পারেন না, অন্যে পরে কা কথা। কাজেই তাদের ল্যাটিনের শরণাপন্ন হতে হয়, কেননা সেই ভাষার প্রসাদে তাদের মনের ময়লা কেটে যায়। সে যাই হোক, আসল ঘটনা এই যে, ইউরোপের লোকভাষাসকল যেদিন ল্যাটিন ভাষার প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলে সেই দিন ইউরোপের মধ্যযুগের অবসান হয়ে নবযুগের সূত্রপাত হল। এক কথায় ইউরোপীয়দের মতে সেই শুভদিনে ইউরোপের মনের রাত কেটে গিয়ে সেখানে দিনের আলো দেখা দিলে।
৫.
মৃতভাষার অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করবামাত্র দেশি ভাষা সব সময়ে একেবারে আত্মবশ হয়ে উঠতে পারে না, অনেক ক্ষেত্রে তা আবার একটি বিদেশি ভাষার শাসনাধীন হয়ে পড়ে। কোনো দেশের উপর বিদেশির রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব সেই দেশীয় ভাষার উপর বিদেশীয় ভাষার প্রভুত্বের একটি স্পষ্ট ও প্রধান কারণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি বিদেশি ভাষা সরকারি ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বিজিত জাতির ভাষা ও সাহিত্যের উপর জয়লাভ করতে পারে না। গ্রীস রোমের অধীন হয়েও পুরাকালে ভাষায় ও সাহিত্যে তার স্বরাজ্য সম্পূর্ণ রক্ষা করেছিল। ফারসিও এ দেশে বহুকাল সরকারি ভাষা ছিল, কিন্তু আমাদের ভাষার উপর ফারসি ভাষার এবং আমাদের সাহিত্যের উপর ফারসি সাহিত্যের প্রভাব একরকম নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। অপর পক্ষে এমনও দেখা যায় যে, একটি বিদেশি ভাষা রাজভাষা না হয়েও অপর ভাষার উপর একাধিপত্য করেছে। বিজিত গ্রীসের সাহিত্যের হাতের নীচেই রোমের ল্যাটিন সাহিত্য গড়ে ওঠে। একালের ইউরোপেও এ সত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কিছুদিনের জন্য ফরাসি ভাষা ইউরোপে একরা ভাষা হয়ে উঠেছিল, ইউরোপের প্রায় সকল প্রদেশের সাহিত্যই এক যুগে ফরাসি সাহিত্যের প্রতাপে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।
কিন্তু ইউরোপের সাহিত্যের ইভলিউশনে ইতালির রিভার্শন reversion যথার্থ ই একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। যারা জীবজগতের ইভলিউশন-তত্ত্ব অবগত আছেন তারাই জানেন যে, জীবের ক্রমোন্নতির ধারা একরোখাও নয়, একটানাও নয়। ইভলিউশনের সঙ্গেসঙ্গে রিভার্শন, উন্নতির পিঠ-পিঠ অবনতিও দেখা দেয়। কিছুদূর এগিয়ে তার পর পিছু হটা বোধ হয় মানবসভ্যতারও নৈসর্গিক ধর্ম, নচেৎ যে ভাষায় দান্তে পেত্রার্ক। বোক্কাচ্চিয়ো মাকিয়াভেল্লি প্রভৃতি জগবিখ্যাত লেখকেরা কাব্যে ও ইতিহাসে সাহিত্যের অক্ষয়কীর্তিসকল রেখে গিয়েছেন, সেই ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি ভাষার আনুগত্য স্বেচ্ছায় বরণ করে নিত না। ইতালির নবযুগের আদিকবি আফিয়েরি Alfieri তাঁর আত্মকথায়। লিখেছেন যে, তিনি তার স্বকালের সাধুপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে ফরাসি ভাষাতেই নাটক রচনা করতেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ক্রমে তার এই জ্ঞান জন্মাল যে, সেসকল নাটক কাব্য নয়, শ্রীহীন শক্তিহীন প্রাণহীন কাঠের পুতুল মাত্র। এ কথা শুনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম-বয়সের কথা মনে পড়ে ইতালির সাহিত্যের খবর আমরা বড়-একটা রাখি নে; তার কারণ, ইতালি আল্পস পর্বতের এপারের দেশ, অর্থাৎ আমাদের এদিকের দেশ। আমাদের বিশ্বাস, একালের ইতালীয়েরা পারে শুধু রাস্তায় রাস্তায় অর্গান বাজাতে, আর রংবেরঙের মিষ্টান্ন তৈরি করতে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের হাতে কাব্যের অর্গানও যে চমৎকার বাজে, এবং দর্শনের মিষ্টান্নও যে সুন্দর তৈরি হয়, তার প্রমাণ দানুনদজিয়ো D’Annunzio এবং Benedetto Croce বেনেদেত্তো ক্রোচের দক্ষিণ হস্তের কীর্তি।
যে মার্টিন লুথারের প্রচণ্ড আক্রমণে রোমান চর্চ ও ল্যাটিন ভাষার সর্বজনীন প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল, সেই মার্টিন লুথারের স্বদেশ জর্মানির সাহিত্যও আবার পালটে ফরাসি সাহিত্যের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দী ছিল ফরাসি সাহিত্যের একটি স্বর্ণযুগ। এই সাহিত্যের প্রভাব জর্মানির শিক্ষিত মনকে প্রায় এক শ বৎসরের জন্য একেবারে অভিভূত ও মায়ামুগ্ধ করে রেখেছিল। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ফরাসি সাহিত্যের অনুকরণে জর্মানিতে যে সাহিত্য রচিত হয়, তার কোনোরূপ মূল্য কোনোরূপ মর্যাদা নেই। এই ফরাসি সাহিত্যের গুণে ফরাসি ভাষাও জর্মানদের কাছে একটি নব ক্ল্যাসিক হয়ে ওঠে। নব জর্মানির আদিকর্তা ফ্রেডারিক দি গ্রেট নিজের রসনা ও লেখনীকে সক্লেশে ফরাসি ভাষাতেই বলতে ও লিখতে শিখিয়েছিলেন, অর্থাৎ যিনি ইউরোপে জর্মান জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, স্বয়ং তিনিই বাহোসে বাহালতবিয়তে এবং খোশমেজাজে ফরাসি সাহিত্য ও ফরাসি ভাষার সার্বভৌমিক আধিপত্য শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।।
কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্যের বিষয় আছে। শুনতে পাই, জগদূবিখ্যাত জর্মান দার্শনিক লাইবনিৎস্ Leibnitz এই যুগে তার দার্শনিক গ্রন্থসকল ফরাসি ভাষাতেই রচনা করেন সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসে যে, তাঁর মাতৃভাষা দর্শনরচনার পক্ষে উপযোগী নয়। এ বিশ্বাস যে কতদূর অমূলক তার প্রমাণ তার পরবর্তী এবং ইউরোপের নবযুগের অদ্বিতীয় দার্শনিক কান্টের গ্রন্থসকল। সেসকল গ্রন্থ যে এ যুগের দর্শনশাস্ত্রের ক্ল্যাসিক হয়ে উঠেছে শুধু তাই নয়, কাণ্টের রচনার প্রসাদে ইউরোপের মনে এমন একটি ধারণা জন্মে গেছে যে, জর্মান ভাষাই হচ্ছে দর্শন রচনা করবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ভাষা। অতএব দেখা গেল, মার্টিন লুথার যেমন প্রথমে ল্যাটিনের হাত থেকে উদ্ধার করে জমান ভাষাকে পায়ের উপর দাঁড় করান, কান্ট তেমনি পরে স্বভাষাকে ফরাসির অধীনতা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সে ভাষাকে নিজের পায়ে চলতে শেখান। স্বভাষায় আত্মপ্রকাশ করবার স্বাধীনতা লাভ করে জর্মান সাহিত্য যে কতদূর ঐশ্বর্য লাভ করেছে, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, এই এক শত বৎসর হচ্ছে জর্মান সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এ যুগের সাহিত্যবথীদের নামের ফর্দ দিতে হলে পুঁথি অসম্ভবরকম বেড়ে যায়, এবং সে ফর্দ দেবারও কোনো দরকার নেই। কাব্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে জর্মান মহারথীদের নাম শিক্ষিতসমাজে কার নিকট অবিদিত? জর্মান প্রতিভার এই আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব বিকাশের প্রত্যক্ষ কারণ এই যে, জর্মান ভাষা এবং সেই সঙ্গে জর্মান আত্মিা তার স্বরাজ্য লাভ করেছে।
৬.
অপর পক্ষে, যে গুণে ফরাসি ভাষা রুশীয় জর্মান প্রভৃতি ভাষার উপর প্রভুত্ব করেছে, সেই গুণেই তা এযাবৎ স্বীয় সুনীতি ও সুরুচি রক্ষা করে এসেছে। ফরাসি হচ্ছে বড় ঘরের সন্তান, প্রাচীন ল্যাটিনের বংশধর; সুতরাং এ ভাষা তার আত্মজ্ঞান কখনোই হারায় নি, তার আভিজাত্যের অহংকারই তার আত্মরক্ষার কারণ হয়েছে। ফরাসি প্রভৃতি ল্যাটিন জাতিরা বহুকাল যাবৎ জর্মানদের বর্বর বলেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে এসেছিল। বর্বর শব্দের মৌলিক অর্থ হচ্ছে সেই জাতি, যার ভাষা বোঝা যায় না। সুতরাং এ জাতি যে কস্মিনকালেও অজ্ঞাতকুলশীল জর্মান ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করে নি, তা বলা বাহুল্য।
এমনকি, যে জর্মান দর্শন গত শতাব্দীতে পৃথিবীর শিক্ষিতসমাজের মনের উপর একছত্র এবং অখণ্ড রাজত্ব করেছে সে দর্শনও ফরাসি মনকে বেশিদিন আত্মবশে রাখতে পারে নি। প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক তেইন গত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মত প্রকাশ করেন যে, জর্মানি তৎপূর্ববর্তী এক শ বৎসর যা চিন্তা করেছে, তৎপরবর্তী এক শ বৎসর সমগ্র ইউরোপকে সেই চিন্তার পুনশ্চিন্তা করতে হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী যে খেটেছে, তার প্রমাণ আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েই পাই। এ যুগের যে ইংরেজি দর্শন আমরা চর্চা করি, তা যে গত যুগের জর্মান দর্শনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, তার পরিচয় নবকান্টিয়ান, নব-হেগেলিয়ান প্রভৃতি নামেই পাওয়া যায়। আমরা দূর-এশিয়াবাসী হয়েও জর্মান দর্শনকে দূরে রাখতে পারি নি; বরং সত্য কথা বলতে হলে, গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমরাও শুধু জর্মানির তৈরি বৈজ্ঞানিক খাদ্য উদরস্থ করছি, আর তার জাবর কাটছি। মনোজগতে যে ল্যাটিন নামক একটি প্রদেশ আছে যা কুয়াশায় ঢাকা নয়, এ কথা আমরা নিজেরা আলোর দেশের লোক হয়েও একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। একবর্ণ জর্মান না জেনেও Nietsche নিশের বই আমরা অনেকেই পড়েছি এবং তার কথার দুকূল-ভাসানো বন্যায় হাবুডুবুও খেয়েছি, কিন্তু ফরাসি দার্শনিক Guyot গুইয়ের নাম আমরা অনেকেই শুনি নি, যদিচ উভয়েই মনোরাজ্যে একই পথের পথিক; দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে, যে পথে ফরাসি গুইয়ো ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন, সেই পথে জর্মান নিশে তাণ্ডবনৃত্য করেছেন। নকুলীশ-পাশুপতদর্শনে দেখতে পাই যে, পাশুপতসম্প্রদায়ের সাধনমার্গে উপহারসংজ্ঞক ছয় প্রকার ক্রিয়া ছিল। তার মধ্যে প্রধান চারটি হচ্ছে, হা হা করে হাস্য করা, গন্ধর্বশাস্ত্রানুসারে গীত গাওয়া, নাট্যশাস্ত্রানুসারে নৃত্য করা এবং হুড়কার করা অর্থাৎ পুঙ্গবের ন্যায় চীৎকার করা। নিশের লেখা পড়ে আমার মনে হয় যে, নকুলীশ-পাশুপতদর্শন ভারতবর্ষে তার ভবলীলা সংবরণ করে জার্মানিতে আবার পুনর্জন্ম লাভ করেছে। গ্যেটে এবং কান্ট সাহিত্যের জগদ্গুরু হলেও এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বিশ্বমানবের মনের উপর আধুনিক জর্মান মনের প্রভাব যেমন অকারণ তেমনি মারাত্মক; কেননা জর্মান দর্শন অপর জাতির মনের আকাশ ঘুলিয়ে দেয়; জর্মান আত্মার। অশেষ গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে কুয়াশা সৃষ্টি করবার শক্তি, এবং সে কুয়াশার গতিরোধ করাও যেমন কঠিন, তার প্রকোপে মনের স্বাস্থ্যরক্ষা করাও তেমনি কঠিন। এ সত্য ফরাসি জাতিই সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করে। যে সময়ে জর্মান আত্মা আমাদের ঘাড়ে চড়তে শুরু করে, ঠিক সেই সময়ে তা ফরাসিদের ঘাড় থেকে নেমে যেতে শুরু করে। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তেইন-এর একটি ধনুর শিষ্য মরিস বাররে Maurice Burrés ল্যাটিন মনের উপর জর্মান মনের এই বিজাতীয় উপদ্রবের উচ্ছেদকল্পে লেখনী ধারণ করেন। যে পুস্তকে তিনি মনোজগতে জর্মান শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন, সে পুস্তকের নাম। Under the Eyes of the Barbarias। জর্মান জাতির আদিম বর্বরতা যে এ যুগে বৈজ্ঞানিক বর্বরতার আকার ধারণ করেছে, বর্তমান যুদ্ধের বহু পূর্বে তা ফরাসি মনীষীদের কাছে ধরা পড়ে, এবং তাও এক হিসেবে ভাষাসূত্রে। জর্মান সাহিত্যের ফরাসি পাঠকের হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, জর্মান অভিধানে এমন একটি কথা আছে, যা ফরাসি অভিধানে নেই, এবং সে হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। অপর পক্ষে জর্মান অভিধানে liumanity শব্দের সাক্ষাৎ অণুবীক্ষণের সাহায্যেও লাভ করা যায় না। মাতৃভাষা জাতির পৈতৃক প্রাণরক্ষার পক্ষে যে কতদূর সহায়, তারই প্রমাণস্বরূপ, ঈষৎ অবান্তর হলেও, এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম।
৭
আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, লোকভাষা মৃতভাষা এবং বিদেশিভাষার অধীনতাপাশ মোচন করতে পারলেও অক্লেশে সম্পূর্ণ আত্ম প্রতিষ্ঠ হতে পারে না। মৌখিক ভাষার স্বরাজ্যলাভের তৃতীয় পরিপন্থী হচ্ছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষা, অর্থাৎ সাধুভাষা। এ বিষয়ে এ প্রবন্ধে আমি বেশি বাক্যব্যয় করতে চাই নে, কেননা ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আমি বহু বক্তৃতা করেছি। সেসব কথার পুনরুক্তি করা এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে প্রেয়ও নয়, শ্রেয়ও নয়; তবে কথাটা একেবারে হেঁটে দিলে এ প্রবন্ধের অঙ্গহানি হয়, এই কারণে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আমার মত বিবৃত করতে বাধ্য হচ্ছি।
মানুষে মৃতভাষা ত্যাগ করে যখন প্রথমে লোকভাষা অর্থাৎ মৌখিক ভাষায় লিখতে আরম্ভ করে, তখন সেই মৃতভাষার রচনাপদ্ধতির আদর্শে ই রচনা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এর উদাহরণও ইউরোপীয় সাহিত্যে। পাওয়া যায়। পদে ও বাক্যে ল্যাটিনিজমের আমদানি ইংরেজির আদি গদ্যলেখকেরাও যথেষ্ট করেছিলেন। সুতরাং আমরাও যে তা করব, সে তো নিতান্ত স্বাভাবিক। বাংলা গদ্যের বয়েস সবে এক শ বছর হলেও তা এক যুগ পিছনে ফেলে এখন দ্বিতীয় যুগে চলছে। প্রথম যুগে সংস্কৃত গদ্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে বাংলা গদ্য লেখা হত। যে যুগ চলছে, তাতে বাংলা গদ্য গঠিত হয়েছে ইংরেজি বাক্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে। আমার বিশ্বাস, এখন আমরা তার তৃতীয় যুগের, অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার যুগের, মুখে এসে পৌঁছেছি। আমার এ বিশ্বাস ভুল হতে পারে, কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে, পরভাষার অনুকরণে এবং উপকরণে যে লিখিত ভাষা গঠিত হয়, সেই পুঁথিগত ভাষা অনেক অংশে নির্জীব। তার পর আরএকটি কথা আছে। যার জীবন আছে, তার নিত্যনূতন বদল হয়। জীবন হচ্ছে একটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের স্রোত মাত্র; সেই কারণেই জীবন্ত ভাষা ক্রমপরিবর্তনশীল, এবং যুগে যুগে তা নূতন মূর্তি ধারণ করে; অপর পক্ষে লিখিত ভাষা অক্ষরের মধ্যে অক্ষয় হয়ে বসে থাকে। নৈসর্গিক কারণেই লিখিত ভাষার কাছ থেকে কথিত ভাষা কালবশে এতটা দূরে সরে যায় যে, সে দুই ভাষা প্রায় দুটি বিভিন্ন ভাষা হয়ে ওঠে। তখন মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার সেই প্রাচীন বিবাদ আবার নূতন আকারে দেখা দেয়; কেননা পূর্বযুগের লিখিত ভাষা পরযুগের কাছে সম্পূর্ণ মৃত না হলেও অর্ধমৃত তো বটেই। মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার বিরোধের চাইতে সাধুভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার কলহের কলরবটা কিছু বেশি, কেননা এ হচ্ছে জ্ঞাতিশত্রুতা। তা ছাড়া লিখিত ভাষাই হচ্ছে সাহিত্যজগতে মৌখিক ভাষার যথার্থ শিক্ষাগুরু। সুতরাং মৌখিক ভাষার পক্ষে সাহিত্যরাজ অধিকার করবার প্রয়াসটা সত্যসত্যই শিষ্যের পক্ষে গুরুকে ছাড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা। এ অবস্থায় সাহিত্যের দ্রোণাচার্যেরা যে সাহিত্যের একলব্যদের অঙ্গুলিচ্ছেদের আদেশ দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি। এতে অবশ্য ভয় পেলে স্বভাষাকে স্বরা করে তোলা যাবে না। এ কথাটা শ্রুতিকটু হলেও সত্য যে, গুরুভক্তি না থাকলে যেমন সনাতন বিদ্যা অর্জন করা যায় না, তেমনি গুরুমারা বিদ্যে না শিখলেও নূতন সাহিত্যের সর্জন করা যায় না। প্লেটো-অ্যারিস্টটলের যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যের ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। অতএব বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার যুদ্ধটা নিরর্থকও নয়, নিষ্ফলও নয়। মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার, বিদেশি ভাষার সঙ্গে স্বদেশি ভাষার লড়াইও তো ঐ বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার জীবনসংগ্রাম বই আর কিছুই নয়।
৮.
ইউরোপ হতে সংগৃহীত এই ইতিহাসের আলোক বঙ্গভাষার উপর ফেলে দেখা যাক, আমাদের মাতৃভাষার বর্তমান অবস্থাটা কি। বঙ্গভাষার পুরাতত্ত্ব আজও পুরো জানি নে; কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস আমাদের কাছে একেবারে অবিদিত নয়। এ ইতিহাসের দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ অধ্যায় আছে। আমাদের সাহিত্যের যে যুগ গত হয়েছে সেটিকে নবাবি যুগ, এবং যে যুগ আগত হয়েছে সেটিকে সাহেবি যুগ বলা যায়।
নবাবি যুগের সাহিত্যে, ছড়া পাঁচালি পদাবলী ও সংস্কৃত কাব্যের প্রাকৃত অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না; এক কথায় এ সাহিত্য হচ্ছে পছে লেখা গান ও গল্পের সাহিত্য। কিন্তু নবাবি আমলে বাঙালি যে একমাত্র উদরান্ন ব্যতীত অপর কোনো বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করে নি, এ কথা সত্য নয়। সে যুগে এ দেশে ধর্মশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চা ছিল। জনরব যে, মনুসংহিতার মর্থমুক্তাবলীর রচয়িতা কুল্লুকভট্ট তাহিরপুরের রাজবংশের, এবং কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা উদয়নাচার্য ভাদুড়িকুলের আদিপুরুষ। এ প্রবাদ সত্য বলে গ্রাহ্য করে নেবার দিকে আমার মনের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে, কেননা আমি জাতিতে বারেন্দ্ৰব্ৰাহ্মণ। তৎসত্ত্বেও প্রমাণের অভাবহেতু এ কিংবদন্তিতে কোনোরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু বাঙালির হাতে যে একটি নব্যন্যায় এবং একটি নব্যস্মৃতি গড়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশজাত এসকল সংস্কৃতশাস্ত্রের মূল্য যে কি, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমার জনৈক দ্রাবিড় বন্ধু বলেন যে, বাংলার নব্যন্যায় যে নব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ন্যায় কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। অষ্টাদশতত্ত্ব রচনা করে রঘুনন্দন বাঙালি জাতির উপকার কি অপকার করেছেন সে বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদের অবসর আছে। কিন্তু এইসকল গ্রন্থই প্রমাণ যে, নবাবি আমলেও বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে নি, এবং বাঙালী সমাজতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে বিচার করতে কখনোই ক্ষান্ত হয় নি। কিন্তু সে যুগে আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার একমাত্র বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা, যেমন মধ্যযুগে ইউরোপের ছিল ল্যাটিন। সেকালে বুদ্ধিবিদ্যার বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করবার লোকভাষার কোনোই অধিকার ছিল না। সুতরাং ইংরেজ অসার পূর্বে এ দেশে বাংলা ছিল, মধ্যযুগের ইউরোপে যাকে বলত একটি vulgar tongue, অর্থাৎ ইতর ভাষা।
ইংরেজি অমিলে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু আমাদের দর্শনবিজ্ঞানের বাহন আজ সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজি হয়েছে। কথাটা যে সত্য তার প্রমাণস্বরূপ দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি দেশপূজ্য মনীষিগুণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসকল ইংরেজি ভাষাতেই রচনা করেন। অর্থাৎ লাইনিংসের যুগে জর্মান ভাষার যে অবস্থা ছিল, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে। সাহিত্যের স্কুলে আজও তা প্রমোশন পায় নি, তার ইতরতার কলঙ্ক আজও ঘোচে নি।
৯.
বলা বাহুল্য, বঙ্গসাহিত্য যতদিন কেবলমাত্র গল্প ও গানের গণ্ডির ভিতর আটক থাকবে, ততদিন শিক্ষতসমাজে বঙ্গভাষা যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে। পারবে না। কেননা শ্রেষ্ঠ কাব্য সাহিত্যের মুকুটমণি হলেও সস্তা কথা ও গাঁথা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। নিকৃষ্ট কাব্যসাহিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে কোনো সাহিত্যেরই গৌরব বৃদ্ধি হয় না, এবং অক্ষম হস্তের অযত্নপ্রসূত গান ও গল্প প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় না; কেননা যথার্থ কাব্যসৃষ্টির জন্য চাই স্রষ্টার প্রাক্তন সংস্কার এবং অসামান্য প্রতিভা। এবং সকলেই অবগত আছেন যে, প্রতিভাশালী লেখক এবেলা-ওবেলা হাটে-বাজারে মেলে না। হালে বঙ্গসাহিত্যের একটি নূতন চাল দেখে আমি ঈষৎ ভীত হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্মকীর্তন ও রসতত্ত্ববিচারের বেজায় ধুম পড়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য ভয়ের কোনো কারণ থাকত না, যদি না সাহিত্যে রসের লোভে তার সারের দিকটা উপেক্ষা করবার একটা সম্ভাবনা এসে পড়ত। কদলীবৃক্ষের অন্তরে সার নেই, আছে কেবল রস; সে কারণ আমরা যদি বঙ্গসাহিত্যে সেই নিটোল সুগোল মসৃণ চিক্কণ নধর সরস বৃক্ষের চাযের প্রশ্রয় দিই, তাহলে বঙ্গসরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলীভক্ষণই লেখা আছে। এ স্থলে আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ভাষার উৎপত্তি কর্মে, আর তার পরিণতি জ্ঞানে। ভাষা ব্যতীত মানুষের চিন্তা প্রকাশ করবার অপর কোনো উপায় নেই। অপর পক্ষে আমরা যাকে বলি রস, আর ইংরেজরা ইমোশন, সে বস্তু প্রকাশ করবার নানা উপায় আছে, যথা, স্বেদ কম্প মূর্ছা বেপথু শীৎকার চিৎকার প্রভৃতি। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান ও চিন্তার বাহন হয়েই ভাষা তার স্বরূপ ও স্বরাজ্য লাভ করে। সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে কাব্য, কেননা একমাত্র কাব্যেই জ্ঞানের ভাষা কর্মের ভাষা ও ভক্তির ভাষা, এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসংগম হয়। তিনিই যথার্থ কবিপদবাচ্য, যার হৃদয়রসের সঙ্গে বহুলপরিমাণে জ্ঞানের সার, যার বুকের রক্তের সঙ্গে অনেকখানি মনের ধাতু অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত থাকে। সত্য ও সুন্দর যে কারও কারও হাতে একই বস্তু হয়ে ওঠে, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ কালিদাস শেল্পীয়ার দান্তে মিল্টন গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাকবিদের কাব্য।
সুতরাং বর্তমান অজ্ঞান অবস্থা আমাদের কাছে মোটেই সন্তোষজনক নয়। বঙ্গসরস্বতী কালে যে আমাদের মনোজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হবেন, এই দুরাশাই আমাদের উচ্চ আশা। অতএব কি অবস্থায় এবং কি কারণে লোকভাষা পরবশ হয়ে পড়ে, আর কি অবস্থায় এবং কি উপায়ে তা আত্মবশ হয়ে ওঠে, তারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। অবস্থা বুঝলে তার ব্যবস্থা করা সহজ। মাতৃভাষাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবার লোভ যে আমরা কিছুতেই সংবরণ করতে পারি নে, তার কারণ আমরা জানি যে ‘সর্বম্ আত্মবশং সুখ’ আর ‘সর্বং পরবশং দুঃখম্।
১০.
জীবন্ত ভাষার উপর মৃতভাষার প্রভুত্বের কারণ নির্ণয় করবার জন্য ল্যাটিনের উদাহরণ নেওয়া যাক। পুরাকালে ল্যাটিন যে ইউরোপের পশ্চিমভাগের উপর একাধিপত্য করেছিল তার কারণ, সেকালে ল্যাটিন ছিল সে ভূভাগের রাজভাষা। গ্রীক ভাষা সে যুগের রোমানদের বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হলেও সে ভাষা রাজভাষা নয় বলে রোমের অধীনস্থ অপর দেশসকলে তা অপরিচিত ছিল। তবে রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরও ল্যাটিন যে আর এক হাজার বছর ধরে ইউরোপে নির্বিবাদে প্রভুত্ব করে, তার কারণ রোম তার রাজত্ব হারিয়ে স্বর্গত্ব লাভ করল; যে রোম ছিল প্রাচীন যুগের কর্মরাজ্যের কেন্দ্র, সেই রোম হয়ে উঠল মধ্যযুগের ধর্মরাজ্যের ‘ইটারন্যাল সিটি” অর্থাৎ অমরাপুরী। এক কথায়, রোমানরা খৃস্টধর্ম অবলম্বন করবার পর ল্যাটিন হল দেবভাষা। কোনো বিশেষ ধর্মের ভাষা, অর্থাৎ যজনযাজন ধ্যানধারণা উপাসনা-আরাধনা তন্ত্রমন্ত্র স্তবস্তোত্রের ভাষা যে সেই ধর্মাবলম্বী লৌকিক মনের অলৌকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে, বিশেষতঃ সে ভাষার অর্থ যদি জনগণের জানা না থাকে, এ সত্য তত জগবিখ্যাত। ল্যাটিনের প্রতাপ। ইউরোপে আজও অক্ষুণ্ণ থাকত, যদি না রেনেসাঁ এবং রিফর্মেশন ইউরোপের মনকে রোমান চার্চের একান্ত বশ্যতা থেকে মুক্ত করত। মধ্যযুগের শেষভাগে গ্রীক সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গেসঙ্গে ইউরোপ মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও স্বােপার্জিত জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করলে। এর ফলে, রোমের ধর্মমন্দিরের অটল ভিত টলটলায়মান হল, এবং সেই সঙ্গে ল্যাটিন ভাষারও দৈবশক্তি লোপ পাবার উপক্রম হল। গ্রীক ভাষার প্রভূত ঐশ্বর্য ও অপূর্ব সৌন্দর্যের তুলনায় ল্যাটিন ভাষা ইউরোপের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের চোখে ক্ষীণসত্ত্ব ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ল। এই গ্রীক সাহিত্যের চর্চায় সে যুগের মনীষিগুণ নূতন দর্শনবিজ্ঞানের সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত দর্শনবিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মতন্ত্রকে বিচলিত করতে পারলেও বিপর্যস্ত করতে পারে না। এক ধর্মমতের স্থান অধিকার করতে পারে শুধু আর-এক ধর্মমত। তাই লুথারের প্রবর্তিত রিফর্মেশনই জর্মানিক ভাষাসমূহকে ল্যাটিনের অধীনতা থেকে যথার্থ মুক্তি দান করলে।
১১.
লুথার যেদিন জর্মানির লোকভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করলেন, সেই দিনই জর্মান সাহিত্যের পাকা বুনিয়াদের পত্তন হল। ভাষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, এ সত্য সকলের নিকট সুস্পষ্ট না হলেও নিঃসন্দেহ। মানুষের মনের বাইরে ভাষা নেই, এবং ভাষার বাইরেও মন নেই। ভাষা ও মন হচ্ছে একই বস্তুর অন্তর ও বাহির। সুতরাং ধর্মমত ভাষান্তরিত হলে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ইউরোপ খৃস্টধর্ম অবলম্বন করবার অব্যবহিত কাল পরেই সে দেশে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ খৃস্টসংঘের সৃষ্টি হল, একটি রোমে, আর-একটি কন্স্টান্টিনোপলে। রোমান সাম্রাজ্য তার অধঃপতনের মুখে যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, খৃস্টধর্ম তার অভ্যুত্থানের মুখে ঠিক সেই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এর মূল কারণ যে ভাষার পার্থক্য, তার পরিচয় এ দুটি সংঘের নামেই পাওয়া যায় : একটির নাম গ্রীক চর্চ, অপরটির রোমান। নিউ টেস্টামেন্ট যদি গ্রীক, অর্থাৎ ইউরোপের ভাষায় লেখা না হত, তাহলে এশিয়ার ধর্ম ইউরোপে গ্রাহ্য হত কি না সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। ভাষার শক্তিতে আমি এতটাই বিশ্বাস করি। এ দেশের বৌদ্ধধর্মও যে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তার মূলেও ছিল ঐ ভাষার পার্থক্য : মহাযানের ভাষা সংস্কৃত, এবং হীনযানের পালি।
অপর পক্ষে পৃথিবীতে যখন কোনো নূতন ধর্মমত জন্মলাভ করে, তখন তার বাহন হয় একটি নূতন ভাষা। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল পালিতে, এবং জৈনধর্ম মাগধী প্রাকৃতে; সুতরাং লুথার যখন খৃস্টধর্মের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করলেন, তখন তাকে ল্যাটিন ত্যাগ করে জর্মান ভাষারই আশ্রয় নিতে হল। তিনি এ উপায় অবলম্বন না করলে প্রোটেস্টান্টিজুম ইউরোপে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে কখনই প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারত না। তার প্রমাণ, ল্যাটিনের অপভ্রংশ যাদের মাতৃভাষা, ইউরোপের সেইসকল জাতি আজও রোমান ক্যাথলিক; রোমান ভাষাই রোমান চর্চের সঙ্গে তাদের মনের প্রধান যোগসূত্র। অপর পক্ষে যেসকল জাতির ভাষা জর্মানিক, সেইসকল জাতিই প্রোটেস্টান্ট। একই কারণে বাংলা সংস্কৃতের প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করেছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়েছে। মহাপ্রভু যেদিন ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবধর্মের, জ্ঞান ও কর্মের উপরে ভক্তির প্রাধান্য প্রচার করতে উদ্যত হলেন, সেদিন তাঁকে সংস্কৃত ত্যাগ করে বাংলার আশ্রয় নিতে হল। চৈতন্যের ধর্মসংস্কারকে বাংলাদেশের রিফর্মেশন বলা অসংগত নয়। তার পর এসেছে আমাদের রেনেসাঁ; ইউরোপ একদিন যেমন গ্রীক সাহিত্য আবিষ্কার করে ল্যাটিন ভাষার একাধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করে, আমরাও তেমনি ইংরেজি সাহিত্য আবিষ্কার করে সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য হতে মুক্তিলাভ করেছি, এবং সে একই কারণে। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীক, ধর্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছিল; আমাদের কাছেও ইংরেজি তেমনি, ধর্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছে। ল্যাটিন অবশ্য তাই বলে ইউরোপে বাতিল হয়ে। যায় নি, সে ভাষার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আজও সে দেশে সজোরে চলছে। কিন্তু সে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হিসাবে। অবশ্য রোমান ক্যাথলিক জাতির কাছে সে ভাষা আজও কতক পরিমাণে ধর্মের ভাষা বলে মান্য, কিন্তু প্রধানতঃ বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গণ্য। আমাদের বাঙালিদের কাছে সংস্কৃত আজকের দিনে ঐ হিসাবেই গণ্য ও মান্য।
১২.
অতএব দেখা গেল যে, পরভাষা, তা মৃতই হোক আর বিদেশিই হোক, লোকভাষার উপর প্রভুত্ব করে এই গুণে যে, তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা, এক কথায় বিদ্যাশিক্ষার ভাষা; বলা বাহুল্য, ধর্মের ভাষাও আসলে বিদ্যার ভাষা। অপর বিদ্যার সঙ্গে এ বিদ্যার প্রভেদ এই যে, তা অপর বিদ্যা নয়, তা হচ্ছে। থিয়োলজি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। এই গুণেই ইংরেজি আজ বাংলার উপর প্রভুত্ব করছে। এ প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ভাষা, এক কথায় বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলা। আমাদের উচ্চ আশা এই যে, ভবিষ্যতে বাংলা উচ্চশিক্ষার ভাষা হবে; শুধু বাল্যবিদ্যালয়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ভাষা পাবে প্রথম আসন, এবং ইংরেজি দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করবে। যতদিন বাংলা, হয় বিদ্যালয়ের বহিভূত হয়ে থাকবে, নয় ইংরেজির অনুচর কিংবা পার্শ্বচর হিসাবে সেখানে স্থান পাবে, ততদিন বাংলা সাহিত্য সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব শক্তিশালী হয়ে উঠবে না। এবং বাঙালির প্রতিভাও ততদিন পূর্ণবিকাশ লাভ করবার পূর্ণ সুযোগ পাবে না। সাহিত্যেই জাতীয় মনের প্রকাশ, অতএব সাহিত্যের ঐশ্বর্যেই জাতীয় মনের ঐশ্বর্যের পরিচয়। আমি পূর্বেই বলেছি, ভাষা ও মন একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। বাংলা ভাষাকে বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলবার পথে কত এবং কি গুরুতর বাধা আছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। তৎসত্ত্বেও আমি বলি, সেসকল বাধা আমাদের অতিক্রম করতেই হবে, নচেৎ বাঙালির মন চিরকাল অর্ধপক অবস্থাতেই থেকে যাবে। বঙ্গসাহিত্যের গুরুগম্ভীর প্রবন্ধনিবন্ধাদি পাঠ করলেই দেখা যায় যে, সেসকল রচনা কোনো অংশে পাকা আর কোনো অংশে কাঁচা। এসব লেখার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের একটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। পঠিত পুস্তকের স্মৃতি লেখকদের যেখানে অক্ষুণ্ণ সেখানে লেখা পাকা, আর যেখানে ক্ষুণ্ণ সেখানে কাঁচা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে-মনের পরিচয় পেয়ে ইউরোপ যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই পকষায় মন আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে একান্ত দুর্লভ। এর কারণ, আমাদের মনকে দিবারাত্র পরভাষার জাগ দিয়ে অকালপক্ক করে তোলা হচ্ছে।
বিদ্যালয়ের ভাষা না হলে আমাদের ভাষা যে তার পূর্ণ শ্ৰী পূর্ণ শক্তি লাভ করবে না, এ কথাও যেমন সত্য, অপর পক্ষে আমাদের সাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহিত্য না হলেও যে তা বিদ্যালয়ে গ্রাহ্য হবে না, এ কথাও তেমনি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পত্ৰসূচনায় লিখেছেন
এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, “মহাশয় আপনি বাঙ্গালি বাঙ্গল। গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন?” তিনি উত্তর করেন, “কোন্ বাঙ্গলা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।” আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, যে এ কথার উত্তর নাই।
আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা যদি আমাদের ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তাহলে আমাদেরও, মুক্তকণ্ঠে না হোক, রুদ্ধকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে যে, সে প্রশ্নের উত্তর নেই। তবে আমাদের এ ক্ষেত্রে কর্তব্য যে কি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষায় আমাদের বিদ্যার সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে, এবং সেজন্য বহু শিক্ষিত লোককে কায়মনোবাক্যে বহুদিন ধরে পরিশ্রম করতে হবে। ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাতৃভাষাতেই ইতিহাস এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসকল রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন; কিন্তু সে সাহিত্যের যে তেমন কিছু গৌরব কিংবা সৌরভ নেই তার কারণ, এক দিকে ইংরেজি ভাবের আর-এক দিকে সংস্কৃত ভাষার চাপের মধ্যে পড়ে আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে ভাবতেও পারি নে, মুক্তহস্তে লিখতেও পারি নে।
১৩
উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, মৃতভাষা ও পরভাষার প্রভুত্ব থেকে মাতৃভাষাকে আমি মুক্ত করতে চাই বলে এ ভুল যেন কেউ না করেন যে, আমি সংস্কৃত ও ইংরেজির পঠনপাঠন বন্ধ করে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, তা করলে বঙ্গসাহিত্যে ইভলিউশন হওয়া দূরে থাক্, একটা বিষম ও সম্ভবত ভীষণ রিভার্শন এসে পড়বে। সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা থেকেই আমরা সেই মনের বল ও হাতের কৌশল লাভ করব, যা আমাদের সাহিত্যের মুক্তির কারণ হবে। বর্তমানে ইউরোপের সকল ভাষাই গ্রীক-ল্যাটিনের অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করেছে, কিন্তু তাই বলে সে দেশে গ্রীক-ল্যাটিনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বন্ধ হয় নি। বরং সাহিত্যরাজ্যে ইউরোপের এই স্বদেশি যুগে উপরোক্ত দুটি ক্ল্যাসিকের চর্চা যত গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে, ক্ল্যাসিক-শাসিত যুগে তার সিকির সিকিও হয় নি।
যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ক্ল্যাসিক চর্চা করবার সার্থকতা কি, তাহলে। সে দেশের কাব্যরসের রসিক উত্তর দেবেন যে, ঐ দুটি প্রাচীন ভাষায় যে কাব্যামৃত সঞ্চিত রয়েছে, তার রসাস্বাদ না করলে মানবজনম বিফল হয়; দার্শনিক বলবেন, মনের উদারতা ও হৃদয়ের গভীরতা লাভ করবার জন্য অতীতের সাহিত্যের পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। করতে উদ্যত হবেন যে, অতীতের সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় না থাকলে আমরা বর্তমান সভ্যতার যথার্থ প্রকৃতি ও মতিগতির পরিচয় পাব না, কেননা বর্তমান ক্রমগঠিত হয়েছে অতীতের গর্ভে; এবং আর্টিস্ট দেখিয়ে দেবেন যে, ক্ল্যাসিক সাহিত্যের এমন-একটি গুণ আছে যা বর্তমান সাহিত্যে পাওয়া দুর্ঘট এবং সে গুণের নাম হচ্ছে আভিজাত্য। এসকল উক্তিই সত্য, সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ চর্চা আমাদের চিরদিনই করতে হবে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর অসংখ্য মৃতভাষার মধ্যে গ্রীক ল্যাটিন ও সংস্কৃত, এই তিনটি আর্যভাষাই ক্ল্যাসিক, অপর কোনোটিই নয়। এ স্থানে একটি কথার উল্লেখ করা দরকার। অলংকারশাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে, ইউরোপে গ্রীক-ল্যাটিনের বাণী সেকালে ছিল প্রভুসম্মিত, একালে তা হয়েছে সুহৃদ্সম্মিত; অর্থাৎ আগে যা ছিল বেদবাক্য, এখন তা হয়েছে ন্যায়কথা। আশা করি, কালে সংস্কৃতসরস্বতীর বাণীও আমাদের কাছে তার প্রভুসম্মিত চরিত্র হারিয়ে সুহৃদ্সম্মিত হয়ে উঠবে। তা যে দূর-ভবিষ্যতেও কান্তাবাণী হয়ে উঠবে, সে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। এই তিনটি ক্ল্যাসিকের মহা গুণ এই যে, তার প্রত্যেকটিই পুরুষালি সাহিত্য, মেয়েলি নয়; সে সাহিত্যে আধআধ ভাষ কিংবা গদ্গদ ভাষের স্থান নেই; সে সাহিত্য যেখানে কোমল সেখানে দুর্বল নয়, যেখানে সানুরাগ সেখানে সানুনাসিক নয়। এ কারণেও সংস্কৃতের চর্চা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং অবশ্যকর্তব্য, কেননা বাংলার বাণীর কান্তাসম্মিত হয়ে পড়বার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক এবং রোখ আছে।
আজকের দিনে ইউরোপের কোনো ভাষাই অপর কোনো ভাষার আওতায় পড়ে নেই, সে ভূভাগে এখন সবাই স্বাধীন সবাই প্রধান; অথচ সে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় এই জাতিস্বাতন্ত্রের যুগেও স্বদেশি ভাষা ব্যতীত আরও অন্ততঃ দুটি-তিনটি বিদেশি ভাষা সাগ্রহে এবং সানন্দে শিক্ষা করেন। এর কারণ কি? এর কারণ, সভ্যজগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগং কেউ আর এক-হাতে গড়ে নি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ, বিদেশি ভাষা ও বিদেশি সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিলে। মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুনো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডির মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই যে, মনোরাজ্যে কূপমণ্ডুক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক-না কেন। এবং এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, যে জাতি মনে যতই বড় হোক-না কেন, তার মনের একটা বিশেষ রকম সংকীর্ণতা আছে, এবং তার মনের ঘরের দেয়াল ভাঙবার জন্য বিদেশি মনের ধাক্কা চাই। বিদেশির প্রতি অবজ্ঞা বিদেশি মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে এবং এই সূত্রে জাতির প্রতি জাতির দ্বেষ-হিংসাও প্রশ্রয় পায়। অপরের মনের সম্পর্কে এলে তার সঙ্গে মনের মিল হওয়াটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; কেননা তখন দেখা যায় যে, অপর জাতির লোকরাও আসলে মানুষ, এবং অনেকটা আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং বিদেশি সাহিত্যের চর্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে; আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি। অতএব মনোজগতে যথার্থ মুক্তি লাভ করতে হলে আমাদের পক্ষে বিশ্বমানবের মনের সংস্পর্শে আসা দরকার। সত্য কথা এই যে, মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও কোনো দেশভেদ নেই; আমরা আমাদের মনগড়া বেড়া দিয়ে তার মনগড়া ভাগবাটোয়ারা করি, সত্যের আলোকে এসব অলীক প্রাচীর কুয়াশার মত মিলিয়ে যায়। এ কথা আমি বিশ্বাস করি বলে, আমার মতে আমাদের পক্ষে শুধু ইংরেজি নয়, সেই সঙ্গে ফরাসি এবং জর্মানও শেখা দরকার। ইংরেজি ভাষা অবশ্য সমগ্র ইউরোপের সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তা আমাদের। মনের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে, কিন্তু অনুবাদের মারফত সাহিত্য পড়া গ্রামোফোনের মারফত গান শোনার মত; অর্থাৎ ও উপায়ে মানুষের প্রাণের কথা আমাদের কানে যন্ত্রধ্বনির আকারে এসে পৌঁছয়। সে যাই হোক, আজকের দিনে ইংরেজির চর্চা ত্যাগ করলে বিশ্বমানবের বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার স্বহস্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে। বাংলা আমাদের শিক্ষার প্রধান ভাষা হলে ইংরেজি বাণী আর প্রভুসম্মিত থাকবে না, সুহৃস্মিত হয়ে উঠবে; প্রভু তখন যথার্থ সখা হয়ে উঠবে। আর-একটি কথা বলেই আমার প্রবন্ধ শেষ করব।
১৪
আজকের দিনে ভারতবাসীর মুখে ‘স্বরাজ’ ছাড়া অপর কোনো কথা নেই। দেশের স্বরাজ্য পরের কাছে হাত পেতে পাওয়া যায় কি যায় না, তা আমি বলতে পারি নে। কিন্তু এ কথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, মনের স্বরাজ্য নিজ হাতে গড়ে তুলতে হয়। তার পর দেশের স্বরাজ্য ইংরেজি ভাষার প্রতাপে লাভ করা গেলেও মনের স্বরাজ্য একমাত্র স্বভাষার প্রসাদেই লাভ করা যায়। সুতরাং সাহিত্যচর্চা আমাদের পক্ষে একটা শখ নয়, জাতীয় জীবন গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কেননা এ ক্ষেত্রে যা কিছু গড়ে উঠবে তার মূলে থাকবে জাতীয় আত্মা এবং জাতীয় কৃতিত্ব।
এক জাতের বুদ্ধিমান লোক আছেন যারা বলেন যে, আমাদের পক্ষে একটা বড় সাহিত্য গড়ে তোলবার চেষ্টাটা সম্পূর্ণ বৃথা। তাদের মতে সাহিত্যের অভ্যুদয় জাতীয় অ্যুদয়কে অনুসরণ করে। এবং নিজের মতের সপক্ষে তাঁরা পেরিক্লিসের এথেন্স, অগাস্টাসের নোম, এলিজাবেথের ইংলণ্ড এবং চতুর্দশ লুইয়ের ফ্রান্সের নজির দেখান। এ মত গ্রাহ্য করার অর্থ আত্মার উপর বাহ্যবস্তুর শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করা। কিন্তু অদৃষ্টবাদ মানুষের পুরুষকারকে খর্ব করে, অতএব বিজ্ঞানসম্মত হলেও তা অগ্রাহ্য। সুখের বিষয়, এ মত মেনে নেবার কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। যদি সাহিত্যের অভ্যুদয় একমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর করত, তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জর্মানিতে অমন অপূর্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হত না, কারণ সে যুগে জর্মানির রাষ্ট্রীয় শক্তি শূন্যের কোঠায় গিয়ে পড়েছিল। নেপোলিয়ন যেদিন সমবেত জর্মান জাতিকে পদদলিত করে জেনা নগরে প্রবেশ করেন, সেদিন সে নগরে গ্যেটে হেগেল উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ এদের একজন কাব্যের, আর-একজন দর্শনের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন; কেননা বিজয়ী ফরাসিদের তোপের গর্জন যে এদের যোগনিদ্রা ভঙ্গ করেছিল এ কথা ইতিহাসে লেখে না। আর এ যুগে জর্মান জাতি সাংসারিক হিসাবে অপূর্ব অভ্যুদয় লাভ করেছে কিন্তু জর্মান সাহিত্য সে অভ্যুদয়ের অনুসরণ করে নি। বরং সত্য কথা এই যে, সে দেশে লক্ষ্মীর। আস্ফালনে সরস্বতী পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছেন।
আসল ঘটনা এই যে, যুগবিশেষে দেশবিশেষের জাতীয় আত্মা যখন সজ্ঞান ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন কি সাহিত্য কি সমাজ সবই এক নূতন শক্তি লাভ করে, এক নূতন মূর্তি ধারণ করে। তখন জাতির আত্মশক্তি নানা দিকে নানা ক্ষেত্রে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। পেরিক্লিসের এথেন্স প্রভৃতি এই সত্যের নিদর্শন। কিন্তু এমন হওয়া আশ্চর্য নয় যে, জাতীয় আত্ম প্রবুদ্ধ হয়ে উঠলেও অবস্থার গুণে বা দোষে তা বিশেষ একটা দিকেই মাথা তুলতে পারে, হয় সাহিত্যের দিকে, নয় শিল্পবাণিজ্যের দিকে। সুতরাং জাতি হিসাবে আমরা শক্তিশালী নই বলে আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা যে বিড়ম্বনা, তা হতেই পারে না। তা ছাড়া সাহিত্যের প্রধান কাজই যখন জাতীয় আত্মাকে প্রবুদ্ধ করা, তখন তার অবসর চিরকালই আছে। আমার শেষ কথা এই যে, বাংলার ভবিষ্যৎ ও বাঙালির ভবিষ্যৎ মূলে একই বস্তু।
১৩২৪ অগ্রহায়ণ
বীরবল
আমি সেদিন দিল্লি গিয়ে আবিষ্কার করে এসেছি যে, আর্যাবর্তে আমি ‘বীরবল’ বলে পরিচিত, অবশ্য শুধু প্রবাসী বাঙালিদের কাছে। এ আবিষ্কারে আমি উৎফুল্ল হয়েছি, কি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছি, বলা কঠিন। লেখক হিসেবে আমি যে বাংলার বাইরেও পরিচিত, এ তো অবশ্য আহ্লাদের কথা; কিন্তু আমার ধার-করা নামের পিছনে যে আমার স্বনাম ঢাকা পড়ে গেল, এইটিই হয়েছে ভাবনার কথা। কারণ আমি স্বনামেও নানা কথা ও নানা রকম জিনিস লিখি। এর পর আমি যে কেন ও-নাম আত্মসাৎ করেছি ও বীরবল লোকটি যে কে ছিলেন, সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয়াটা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।
আমি যখন বালক, তখন আমার পিতার কর্মস্থল ছিল বেহার। কাজেই তিনি সেকালে বছরের বেশির ভাগ সময় সেই দেশেই বাস করতেন। আর আমি বাস করতুম বাংলায়, স্কুলে পড়বার জন্য। আমার বিশ্বাস এর কারণ, বাবা মনে করতেন বেহারের আবহাওয়ায় মানুষের মাথা তাদৃশ খোলে না, যাদৃশ ফোলে তার দেহ।
এর ফলে তিনি অপিসের পুজোর ছুটিতে বাংলায় আসতেন, আর আমরা কেউ কেউ বেহারে যেতুম স্কুলের শীতের ছুটিতে।
আমার বয়েস যখন এগারো বৎসর, তখন একবার আমি শীতকালে মজঃফরপুর যাই। সঙ্গে ছিলেন আমার একটি ভ্রাতা ও একটি ভগ্নী। আমিই ছিলুম সবচাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। দিনটে একরকম খেলাধুলায় কেটে যেত। সন্ধের পর বাড়ির জন্য মন কেমন করত।
বাবা তাই ঘরের ভিতর প্রকাণ্ড একটা আঙুঠি জ্বালিয়ে, তার চার পাশে আমাদের বসিয়ে একখানি উছু বই থেকে আমাদের কেচ্ছা পড়ে শোনাতেন। এর অধিকাংশ কেচ্ছাই এই বলে শুরু হত ‘আকবর বীরবল নে পুছা’, আর শেষ হত বীরবলের উত্তরে।
২.
আমি তখন তারিণীচরণের ভারতবর্ষের ইতিহাসের পারগামী হয়েছি, সুতরাং আকবরশাহের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল; অর্থাৎ তিনি যে জাহাঙ্গীরের বাবা ও হুমায়ুনের ছেলে, এ কথা আমার জানা ছিল।
কিন্তু বীরবল লোকটি যে কে, হিন্দু কি মুসলমান, বাদশাহের মন্ত্রী কি ইয়ার, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম; কারণ তারিণীচরণ তার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি।
কিন্তু সেইসব উহু কেচ্ছা শোনাবার ফলে আমার মনে বীরবলের নাম বসে যায়। আকবরের প্রশ্নের উত্তরে বীরবলের চোখাচোখা জবাবু শুনে আমি মনে মনে তার মহাভক্ত হয়ে উঠলুম। প্রশ্ন করতে পারে সবাই, কিন্তু উত্তর দিতে পারে কজন? আর যে পারে, আমার বালক-বুদ্ধি তাকেই প্রশ্নকর্তার চাইতে উঁচু আসনে বসিয়ে দিলে। (মুখের চাইতে হাত যে বড় হাতিয়ার, বুদ্ধিবলের চাইতে বাহুবল যে শ্রেষ্ঠ, সে কথা আমি তখন বুঝতুম না; কারণ সে বয়েসে আমি সভ্য হই নি, ছিলুম শুধু আদিম মানব। সেকালে বাহুবলের একমাত্র পরিচয় পেতুম গুরুজনদের ও গুরুমহাশয়দের বাহুতে। জোয়ান লোকদের কর্তৃক ছোট ছোট ছেলেদের গালে চপেটাঘাত ও কর্ণমদনের মাহাত্ম্য ও-বয়েসে হৃদয়ংগম করতে পারি নি। আমাদেরই ভালোর জন্য যে তারা আমাদের কানের রং লাল করে দিচ্ছেন ও আমাদের গালে তাদের পাঁচ আঙ লের ছাপ দেগে দিচ্ছেন, তা বোঝবার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি তখন আমার ছিল না। এই পরোপকারের চেষ্টাটা সেকালে অত্যাচার বলেই রক্তমাংসে অনুভব করতুম। তাই তখন মনে ভাবতুম, হায়, আমার মুখে যদি বীরবলের রসনা থাকত, তাহলে। এই সব ঘরো আকবরশাহদের বোকা বানিয়ে দিতুম। দুর্বলের উপর বলপ্রয়োগের নামই যে বীরত্ব, তা বুঝলুম ঢের পরে, যখন কালাইলের Hero-Worslip পড়লুম।
৩.
এর পর বহুকাল যাবৎ বীরবলের নাম আমার গুপ্তচৈতন্যে সুপ্ত হয়ে ছিল। আমার যখন পূর্ণযৌবন, তখন আবার তা জেগে উঠল। বিলেতে আমার অনেক মুসলমান বন্ধু জোটে, তাদের কারও বাড়ি লক্ষ্ণৌ, কারও দিল্লি, কারও নাগপুর, কারও হাইদ্রাবাদ। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন আবার
নবাবজাদা।
এই নববন্ধুদের মুখে বীরবলের রসিকতার দেদার গল্প শুনি। এসব রসিকতা যে অন্য লোকের বানানো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা এসব গল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রমাণ করা যে, আকবরের সভায় বীরবলের চাইতেও আর-একজন ঢের বড় রসিক ছিলেন, যিনি কথায় কথায় বীরবলকে উপহাসম্পদ করতেন। এই রসিকরাজের নাম হচ্ছে মৌলবী দো-পিঁয়াজা। উক্ত মৌলবীসাহেবের সুভাষিতাবলী যে সাহিত্যে স্থান লাভ করে নি, তার কারণ তাঁর রসিকতা তার নামেরই অনুরূপ তীব্রগন্ধী, সে রসিকতা শুনে যুগপৎ কানে হাত ও নাকে কাপড় দিতে হয়।
এইসব কেচ্ছা শুনে আমার এই ধারণা জন্মালে যে, বীরবল ছিলেন আকবরশাহের বিদূষক, আর তিনি জাতিতে ছিলেন হিন্দু। বিদূষক হিসেবে তিনি হিন্দুস্থানে দেশব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছিলেন বলে তার পালটা জবাবু দিতে পারে এমন একজন মুসলমান রসিক কল্পিত হয়েছে। তার নামেই প্রমাণ যে, উক্ত নামধারী কোনো মৌলবী আকবরশাহের সভাসদ হতে পারত না।
সে যাই হোক, বছর কুড়িক আগে আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম। এ নামের দুইটি স্পষ্ট গুণ আছে : প্রথমতঃ নামটি ছোট, দ্বিতীয়তঃ শ্রুতিমধুর। এ নাম গ্রহণ করে আমি স্বজাতিকে বাদশাহের পদবীতে তুলে দিয়েছি, সুতরাং তাদের এতে খুশি হবারই কথা। আর মুসলমান ভ্রাতৃগণের কাছে নিবেদন করছি যে, আমি যত বড়ই রসিক হই না কেন, মৌলবী দো-পিঁয়াজার নাম গ্রহণ করা আমার শক্তিতে কুলোয় না। ইংরেজিশিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তান অকাতরে পলা ভক্ষণ করতে পারে, কিন্তু নিজেকে পলাতু বলে ভদ্রসমাজে পরিচিত করতে পারে না। জাতি জিনিসটে এমনি বালাই।
৪.
মৌলবী দো-পিঁয়াজার অস্তিত্ব অসিদ্ধ, প্রমাণাভাবাৎ। কিন্তু বীরবল যে এককালে সশরীরে বর্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই; কারণ আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক মৌলবীসাহেবেরা তার মৃত্যুর বর্ণনা খুব ফুর্তি করে করেছেন। যার মৃত্যু হয়েছে, সে অবশ্য এককালে বেঁচে ছিল। তিনি আকবরশাহের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। ফলে আকবরের বহু প্রসাদবিত্তদের তিনি সমান অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আর ইতিহাসে সেই ব্যক্তিরই নাম স্থান পায়, যে নিন্দা প্রশংসা দুয়েরই সমান ভাগী। বীরবলের ভাগ্যে দুই যে সমান জুটেছিল, তার পরিচয় পরে দেব।
জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক ফারসি ভাষার সব পাজিপুঁথি ঘেঁটে বীরবলের আসল নামধাম উদ্ধার করেছেন। বীরবল নামটিও রাজদত্ত।
বীরবলের প্রকৃত নাম ছিল মহেশ দাস। তিনি ১৫২৮ খৃস্টাব্দে কাল্পি নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান প্রথমে জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের আশ্রয়ে বাস করতেন, পরে রাজাবাহাদুর তাকে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দেন। মহেশ দাসের কবিতা, তার সংগীত, তাঁর রসালাপ, তার গল্প আকবরকে এত মুগ্ধ করে যে, তিনি তাঁকে ‘কবিরায়’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐতিহাসিকেরা তাকে কখনো আকবরের মন্ত্রী, কখনো বা প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। পরে আকবরশাহ তাঁকে ‘রাজা বীরবল’ উপাধি দেন, এবং সেই সঙ্গে বুন্দেলখণ্ডের কালাঞ্জর রাজ্য ও কাংরা প্রদেশ জায়গীর দেন। ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে আকবর বীরবলকে সেনাপতি করে কাবুল-যুদ্ধে পাঠান, এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানদের হস্তে তিনি ভবলীলা সংবরণ করেন।
৫
এইসব তথ্য আমি ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের Akbar The Great Mojul নামক পুস্তক হতে সংগ্রহ করেছি। আমি পূর্বে বলেছি যে, বীরবলের প্রতি মৌলবীসাহেবরা যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, এবং এ অসন্তোষের কারণও ছিল। আবদুল কাদির নামক আকবর শাহের জনৈক ঘোর সুন্নি সভাসদের তারিখ-ইবাদাউনি নামক পুস্তকের একবার পাতা উলটে গেলেই দেখতে পাবেন যে, তার প্রায় পাতায় পাতায় বীরবলের উপর গালিগালাজ আছে। এমনকি, স্বধর্মনিষ্ঠ মৌলবীসাহেব বীরবলের নাম পর্যন্ত মুখে আনেন না, তার পূর্বে ‘দাসীপুত্র’ বিশেষণটি জুড়ে না দিয়ে। মৌলবীসাহেবের রাগের কারণ পরে উল্লেখ করব। এ স্থলে একটি কথা বলে রাখা দরকার। আকবর শাহের আমলের যত ইতিহাস ফারসি থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে তারিখ-ই-বাদাউনিই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এর প্রথম কারণ, মৌলবীসাহেব অত্যন্ত স্পষ্টভাষী; দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মনে রাগদ্বেষ ছিল বলে তাঁর। লেখায় মুন-ঝাল দুই আছে; অপরাপর ইতিহাসের মত পাসে নয়। তা ছাড়া, তার গ্রন্থ ইতিহাস না হোক, সাহিত্য। যদিচ বইখানির নাম তারিখ, তাহলেও সেটি শুধু ক্রনোলজি নয়, অর্থাৎ পাঁজি নয়, পুঁথি। তিনি যাদের নাম করেছেন, তাদেরই চেহারা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। আকবর, আবুল ফজল, ফৈজি, বীরবল প্রভৃতি তার লেখায় শুধু নামমাত্র নয়, রূপবিশিষ্টও বটে। তিনি মহা রাগী পুরুষ ছিলেন; তার জন্য দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই; কেননা কথায় বলে রাগই পুরুষের লক্ষণ। তাঁকে অবশ্য নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বলা যায় না, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ইতিহাসের দরবারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন নি। তিনি ভুল করতে পারেন কিন্তু জেনেশুনে মিছে কথা বলেন নি। বাদাউনি বলেছেন যে, বীরবল প্রথমে রেওয়ার রাজা রামচন্দ্রের আশ্রয়ে ছিলেন, তিনিই বীরবল ও তানসেনকে তাঁর সভার দুটি রত্ন হিসেবে বাদশাহকে উপঢৌকন দেন। এই কথাই, আমার বিশ্বাস, সত্য।
বীরবলের উপর বাদাউনির রাগ বোঝা যায়। কিন্তু স্মিথ সাহেবও যে কি কারণে বীরবলের প্রতি বিরক্ত তা বোঝা কঠিন, কারণ তিনি মুসলমানও নন, মুসলমান প্রণয়ীও নন, তা যে তিনি নন যে-কেউ তার Oxford History of India পড়েছেন, তিনিই জানেন। স্মিথ সাহেব বীরবলকে অবশ্য দাসীপুত্র বিশেষণে বিশিষ্ট করেন না, কিন্তু ফাঁক পেলেই তিনি বীরবলকে আকবরশাহের ভাড় বলে উল্লেখ করেন। যে ব্যক্তি একাধারে কবি গায়ক গল্পরচয়িতা ও সুরসিক, তাকে শুধু জেস্টার বলে উল্লেখ করে স্মিথ সাহেব গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন নি। স্মিথ সাহেব বলেন যে, বীরবল যে আকবরবাদশার। মন্ত্রী ছিলেন, এ কথা ভুল; তিনি অনুমান করেন যে, বীরবল ছিলেন আকবরের আস্তাবলের জমাদার। তার ভাষায় কবিরায়ের ইংরেজি প্রতিবাক্য হচ্ছে পোয়েট-লরিয়েট। টেনিসনকে ইংলণ্ডের রাজা তার অশ্বপালনে নিযুক্ত করেন নি, আর এ দেশে আকবরবাদশা যে তার কবিরায়কে ঘোড়ার খিদমতগারিতে নিযুক্ত করেছিলেন, এমন কথা মৌলবী বাদাউনিও বলেন নি। যদি তিনি করতেন, তাহলে তিনি Akbar the Great হতেন না, হতেন শুধু Akbar the Mogul.
কিন্তু এই অদ্ভুত অনুমানের কারণ আরও অদ্ভুত। আকবর ফতেপুরশিক্রীতে বীরবলের বাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন, সে ইমারত আজও দাঁড়িয়ে আছে। সে বাড়ির বর্ণনা স্মিথ সাহেবের কথাতেই নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—
The exquisite structure at Fathpur-Sikri known as Raja Birbal’s hotiseas erected in 1571 or 1572… The beauty and lavishness of the decoiation testify to the intensity of Akbar’s affection for the Raja…
The proximity of his beautiful house in the palace of FathpurSikri to the stables lias suggested the hypothesis that he may have been Master of Horse.
বিলেতি লজিকের কোন্ সূত্র অনুসারে যে এইরূপ প্রক্সিমিটি থেকে এইরূপ হাইপথেসিস্ এ পৌঁছনো যায়, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিদিত। আমি মিল এর ইন্ডাটিব লজিক পড়ি নি; তাই আস্তাবলের পাশে যার বাড়ি, সেই যে সহিস এ কথা মেনে নিতে আমি কুণ্ঠিত। আলিপুরে লাটসাহেবের বাড়ির পাশেই আছে পশুশালা, এর থেকে লাটসাহেবকে পশুশালার অধ্যক্ষ বলে ধরে নেওয়াটা ঐতিহাসিক বুদ্ধির কাজ হতে পারে, কিন্তু সহজ বুদ্ধির কাজ নয়।
বর্তমান যুগে আমি একটিমাত্র ব্যক্তিকে জানি, যিনি একাধারে কবি দু হাত দূরে আস্তাবল আছে। আমি তার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন ও-আস্তাবল অবিলম্বে ভূমিসাৎ করেন, নচেৎ ভবিষ্যতের স্মিথ সাহেবরা তার সম্বন্ধে কি যে হাইপথেসিস করবেন, তা বলা যায় না।
৬.
আকবর শাহ যেমন শোকাতুর হয়েছিলেন, মৌলবী বাদাউনি প্রভৃতি তেমনি আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। স্মিথ সাহেব এ মৃত্যুকে বলেছেন inglorious death; কারণ যে যুদ্ধে তার প্রাণ যায়, সে যুদ্ধে তার সৈন্যসামন্ত প্রায় সমূলে নিপাত হয়। যুদ্ধে হারাটা দুঃখের বিষয় হতে পারে, কিন্তু সব সময়ে লজ্জার বিষয় নয়। রানী দুর্গাবতী আকবরের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যুদ্ধে হেরেছিলেন ও যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন; অথচ ঐতিহাসিক মাত্রেই তাঁর মৃত্যুকে glorious death বলেছে।
স্মিত সাহেবের বিশ্বাস যে
The disaster appears to have been duc in large part to his folly and inexperience. Akbar made a serious mistake in sending such people as Birbal and the Hakim to command military forces operating in a difficult country against a formidable enemy.
৭.
আকবর শাহের সভাকবি যে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, এ কথা সহজেই মনে হয়। টেনিসনকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠালে যে একটা-না-একটা বিভ্রাট ঘটত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তবে বীরবল তত শুধু কবি ছিলেন না, উপরন্তু তিনি ছিলেন বিদূষক ও গল্পরচয়িতা। ভাসের অবিমারক নামক নাটকে পড়েছি যে, রাজপুত্র তার বিদূষককে হারিয়ে এই বলে দুঃখ করেছিলেন যে, আমার এমন বয়স্য গেল কোথায়, যে ঘরে ছিল নৰ্মসচিব ও যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রগণ্য যোদ্ধা। অতএব বিদূষকও যে যোদ্ধা হতে পারে, তার সংস্কৃত নজির আছে।
আর গল্পরচয়িতাও যে সেনাপতি হতে পারে, তার প্রমাণ টলস্টয় ছিলেন ক্রিমিয়ান ওয় এ রুশ পক্ষের একজন সেনাপতি। সে যুদ্ধে রুশপক্ষ জয়লাভ করে নি; এবং তার জন্য টলস্টয় ইউরোপীয় সমাজে অবজ্ঞার পাত্র হন নি। ক্রিমিয়াতে রুশপক্ষের যত লোক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, তার চাইতে ঢের বেশি সৈন্য প্রাণত্যাগ করে ওলাউঠায়। উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ও-রোগের এমন ভীষণ প্রকোপ হয়েছিল যে, টলস্টয় পাছে ও-রোগে আক্রান্ত হন এই ভয়ে, স্বয়ং জার তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু টলস্টয় সে আদেশ অমান্য করেন এই বলে যে, তিনি তার অধীনস্থ দীনহীন অসহায় সৈনিকদের এই বিপদের মধ্যে ত্যাগ করে নিজের প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করতে প্রস্তুত নন, রাজার হুকুমেও নয়।
সুতরাং কাবুলের যুদ্ধে যে বীরবলের অজ্ঞতা ও কাপুরুষতার দরুনই হার হয়েছিল, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। বিশেষতঃ স্মিথ সাহেব এই ঘটনা যখন আকবরেরও আহাম্মকির প্রমাণস্বরূপ গণ্য করেন, তখন তাঁর মত একেবারেই অগ্রাহ। ধরে নিচ্ছি যে, বীরবলের রসিকতাই আকবরকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ করা যে রসিকতা নয়, তা আর কেউ না জানেন, আকবর জানতেন। আর কোন্ লোকের দ্বারা কোন্ কাজ উদ্ধার হয়, তাও যে তিনি জানতেন, তার পরিচয় তিনি চিরজীবনই দিয়েছেন। সুতরাং স্মিথ সাহেবের it appears’ কথাটার কোনোরূপ ঐতিহাসিক মূল্য নেই। স্মিথ সাহেব কিন্তু শুধু বীরবলকে অজ্ঞ ও অক্ষম বলেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি আরও বলেন যে–
He secins to have frankly run away in a vain attempt to save his life.
8.
স্মিথ সাহেব এ সত্য কোথা থেকে উদ্ধার করলেন? অবশ্য তারিখ-ইবাদাউনি থেকে। সুতরাং মৌলবী সাহেব বীরবলের মৃত্যু সম্বন্ধে কি বলেন, তা তার মুখেই শোনা যাক। বাদাউনির কথা হচ্ছে এই–
Bir Bar also, who had fled from fear of this life, was slain, and entered the row of the dogs in hell, and thus got something for the abominable deeds he had done during his lifetime.
বাদাউনির কথা যদি বেদবাক্য হিসেবে মেনে নিতে হয়, তাহলে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, বীরবল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এক দৌড়ে গিয়ে। নরকের কুকুরের দলে ভর্তি হয়েছিলেন। অর্থাৎ জীবনে যিনি বাস করতেন। ঘোড়ার সঙ্গে, মরে তিনি গিয়ে বাস করতে লাগলেন কুকুরের সঙ্গে। এ ঘটনা যে ঘটেনি তা বলা অসম্ভব, কারণ নরকে যে Birbal’s House ঠিক কোন্ জায়গায়, তা বাদাউনিও নিজচক্ষে দেখেন নি, স্মিথ সাহেবও দেখেন নি। সুতরাং বাদাউনির উক্তির শেষ অংশটা যদি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে অগ্রাহ্য হয়, তাহলে তার প্রথম অংশটা সত্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবসর থাকে।
শাস্ত্রে বলে ‘যঃ পলায়তে স জীবতি’। আর শাস্ত্রবচন যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ উক্ত যুদ্ধক্ষেত্র হতে যে-দুটি মুসলমান সেনাধ্যক্ষ পলায়ন করেছিলেন, তারা দুজনেই বেঁচেছিলেন। এই কারণে এ বিষয়ে আবুল ফজল তাঁর আকবরনামায় যা লিখেছেন, it seeins to me, সেই কথাটাই সত্য। তার কথা এই–
In the conflict 500 men perished. Among them was Rajah Birbal, whose loss the Iimperor greatly deplored.
যদি স্মিথ সাহেব বলেন যে, আবুল ফজলের উক্তি অগ্রাহ, কেননা তাতে বীরবলের প্রতি গালিগালাজ নেই; তাহলে বলি আবুল ফজল বলেছেন যে, বীরবল মরেছেন–আর মরার বাড়া গাল নেই।
৯.
বীরবল কি ভাবে মরেছিলেন— শুয়ে কি বসে, দাঁড়িয়ে কিংবা দৌড়তে দৌড়তে–তা জানবার কোনোরূপ কৌতূহল আমার নেই। আমি জানতে চাই তার জীবন, তার মৃত্যু নয়। কেননা মৃত্যুতে আমরা সবাই এক, শুধু জীবনে বিভিন্ন।
তাঁর মৃত্যুর কথাটা তুলেছি এই জন্য যে, উক্ত ঘটনায় আর পাঁচজনে কতটা আনন্দিত বা দুঃখিত হন, তার থেকে তার চরিত্র কতকটা অনুমান করা যায়।
বীরবলের মৃত্যুসংবাদে আকবর যে শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, সে বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক একই সাক্ষ্য দিয়েছেন। অপরপক্ষে বীরবলের মৃত্যুতে দেশের পাপ গেল মনে করে বাদাউনি প্রমুখ মৌলবীর দল তাদের উল্লাস যে কি রকম তারস্বরে ব্যক্ত করেছিলেন, তার পরিচয় তো বাদাউনির পূর্বোক্ত কথাতেই পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, বীরবল জীবনে যেসকল জঘন্য কাজ করেছিলেন, সেইসব পাপের শাস্তিস্বরূপ তিনি নরকের কুকুরশ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। এই জঘন্য কাজগুলি কি?
আকবরশাহ স্বধর্মের মায়া কাটিয়ে স্বকল্পিত এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন। বাদাউনির বিশ্বাস বীরবলই তাকে ধর্মভ্রষ্ট করে।
আকবরের সভায় মোল্লা মহম্মদ ইয়াজিজি নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে সুন্নি মতের নানারূপ নিন্দা করে বাদশাহকে শিয়া মতাবলম্বী করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, পরে বাদাউনির ভাষায়
This man was soon left behind by Birbal, that bastard, and by Shaik Abul-Fazal.
এঁদের কুপরামর্শে আকবর শাহ কতদূর ধর্মভ্রষ্ট হয়েছিলেন, তার পরিচয় বাদাউনির বক্ষ্যমান কথাগুলিতেই পাওয়া যায়–
The daily prayers, the fasts and prophecies were all pronounced delusions, as being opposed to sense. Reason and not revelation was declared to be the basis of religion.
আর এ সবই বীরবলের কুবুদ্ধিতে। আকবর যে একজন রিজ্নএর ভক্ত অর্থাৎ র্যাশনালিস্ট হয়েছিলেন, এ কথা সহজেই বিশ্বাস হয়। কারণ বৈষয়িক লোকমাত্রেই দার্শনিক হতে গেলেই ন্যাশনালিস্ট হয়। ন্যাশনালিস্ট হলে মানুষের মাথা খোলে না, কিন্তু তার হৃদয় খুব উদার হয়। আকবরেরও তাই হয়েছিল। তিনি র্যাশনালিস্ট হবার পর প্রকাশ্য দরবারে বলেন যে, ‘আমি পূর্বে বহু ব্রাহ্মণকে জোর করে মুসলমান করেছি, আর তারা প্রাণভয়ে সে ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এখন বুঝছি যে, আমি অতি গর্হিত কাজ করেছি।‘ তাঁর এ কথায় সকলেই সায় দেবে।
১০.
ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনের অথবা মতের কি বদল হয়, তাতে অপরের কিছু যায় আসে না, যতক্ষণ সে অপরের ক্রিয়াকলাপের উপর হস্তক্ষেপ না করে। আকবর শাহ তাঁর নব মতানুসারে যেসব হুকুম প্রচার করেন, তার দরুনই স্বধর্ম-নিরত মুসলমানগুণ ক্ষোভে আক্রোশে অধীর হয়ে উঠেছিল। স্মিথ সাহেব তাঁর গ্রন্থে এইসব নব রাজশাসনের যে ফর্দ দিয়েছেন, সংক্ষেপে তার পরিচয় দিচ্ছি—
১ কোনো বালকের ‘মহম্মদ’ এই নাম রাখা হবে না। যদি কারও নাম মহম্মদ থাকে তো তার সে নাম বদলে নতুন নাম দিতে হবে;
২ তাঁর রাজ্যে কোনো নূতন মসজিদ কেউ নির্মাণ করতে পারবে না আর জীর্ণ মসজিদের কোনোরূপ সংস্কার কেউ করতে পারবে না;
৩ তার রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ। আর এ অজ্ঞা অমান্য করবার শাস্তি প্রাণদণ্ড। উপরন্তু বৎসরের তিন শ পঁয়ষটি দিনের মধ্যে এক শ দিন মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ;
৪ তার রাজ্যে দাড়ি কেউ রাখতে পারবে না, সকলকেই তা কামাতে হবে;
৫ পিঁয়াজ রশুন ও গোমাংস ভক্ষণ তার রাজ্যে নিষিদ্ধ;
৬ উপাসনার সময় হিন্দুমুসলমান নিবিচারে সকলকে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণ ধারণ করতে হবে।
এইরকম আরও অনেক খামখেয়ালি রাজাজ্ঞা তিনি প্রচার করেছিলেন। পুঁথি বেড়ে যায় বলে সেসবের আর উল্লেখ করলুম না। স্মিথ সাহেব বলেছেন যে–
The whole gist of the regulations was to further the adoption of Ilindu, Jaina, and Parsce practices, while discouraging or positively probibiting essential Muslim rites.
স্মিথ সাহেব যখন এসকল বিধিনিষেধকে silly regulations বলেছেন, তখন বাদাউনি যে তাকে abominable deeds বলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি। আর র্যাশনালিস্ট-এর এইসব বাদশাহী পাগলামির জন্য বাদাউনি বীরবলকেই প্রধানতঃ দায়ী মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, ফৈজী, আবুল ফজল ও বীরবল, এই তিন গ্রহ একত্র মিলে আকবরের কুবুদ্ধি ঘটায়; আর এ তিনের মধ্যে শনি ছিলেন বীরবল।
১১.
অপরপক্ষে সেকালের হিন্দুরা যে বীরবলের মহাভক্ত ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় কেশবদাসের কবিতায়। আকবর শাহের আমলে তুলসীদাস প্রমুখ অনেক হিন্দি কবির আবির্ভাব হয়, কেশবদাস তাদের অন্যতম। কেশবদাস রামসিংহ নামক বুন্দেলখণ্ডের জনৈক রাজার ভ্রাতা ইন্দ্রজিত সিংহের সভাকবি ছিলেন। তিনি রসিকপ্রিয়া নামক একখানি কাব্য হিন্দি ভাষায় রচনা করেন। হিন্দিভাষীরা এ কাব্যকে আজও হিন্দি কাব্যসাহিত্যের একখানি রত্ন বলে মনে করেন।
বীরবলের মৃত্যুসংবাদ শুনে কেশবদাসের শোক নিম্নলিখিত শ্লোকরূপ ধারণ করে–
পাপকে পুংজ পোবজ কেসব সোককে সংখ শুনে সুষমা মেঁ।
ঝুটকী ঝালরি ঝাঁঝ অলীককে আবঝ জগন জানি জমা মেঁ।
ভেদ কী ভেরী বড়ে ডরকে ডফ কৌতুক ভো কলি কে করম মেঁ।
জুঝত হী বলবীর বজে বহু দারিদ কে দরবার দমামেঁ।
আন্দাজ করছি পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের কথা এই যে–
কেশব পাপপুঞ্জের পাথোয়াজ আর শোকশঙ্খের সুষমা শুনতে পাচ্ছে। মিথ্যা কথার ঈসর বাজছে, আর জানি যে অলীকের আওয়াজ, যেখানেই পশুপাল জমা হচ্ছে সেখানেই শোনা যাচ্ছে। ভেদের ভেরীর ভয়ংকর জোর ডঙ্কা বাজছে। কলি কুকর্মে বড় কৌতুক লাভ করেছে। কিন্তু বহু দরিদ্র লোকের দরবারে বীরবল যুদ্ধ করেছেন ও তাঁর নামের দামামা বাজছে।
হিন্দী ভাষা আমি শিক্ষা করি নি। সুতরাং আমার অনুবাদের মধ্যে এখানে ওখানে ভুল থাকতে পারে। তবে কবি কেশবদাসের মোদ্দা কথাটা বোঝা যাচ্ছে। বীরবলের মৃত্যুতে এক দিকে মিথ্যা কথার ঢাক-ঢোল ও ঘোর ভেদের ভেরী বেজে উঠেছিল। আর সেই ভীষণ ধ্বনির প্রতিধ্বনি ইতিহাসের মধ্যে আজও শোনা যাচ্ছে। অপর দিকে আবার তেমনি শোকশঙ্খের ধ্বনিও লোকের কানে ও মনে বেজে উঠেছিল। বহু দরিদ্রের দরবারে তার সুযশ ঘোষিত হয়েছিল। যার মৃত্যুতে দরিদ্রসমাজে শোকশঙ্খ নিনাদিত হয়, তার জীবনও ধন্য আর তার মৃত্যুও glorious death।
বীরবলের জীবনচরিত সম্বন্ধে উপরে যা নিবেদন করেছি, তার বেশি আর কিছু জানি নে।। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই বুঝতে পারবেন যে, তাঁর নাম অবলম্বন করে আমি কতটা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি। আমি কবিও নই, গায়কও নই, গল্পরচয়িতাও নই। তারপর রাজদরবার আমি কখনো দূর থেকেও দেখি নি। কাবুলে যুদ্ধ করতে যাবার আমার কোনোরূপ অভিপ্রায়ও নেই, সম্ভাবনাও নেই। তার পর আমি কাউকে নূতন ধর্ম প্রচার করতে কখনন প্ররোচিত করি নি। আমি বাঙালি জাতির বিদূষক মাত্র। তবে রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি। কারণ নিত্য দেখতে পাই যে, অনেকে আমার সত্য কথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকতাকে সত্য কথা বলে ভুল করেন।
এখন এ ভুল শোধরাবার আর উপায় নেই। পাঠকেরা যে আমার লেখার ভিতর সত্য না পান, রস পেয়েছেন, এতেই আমি কৃতার্থ।
১৩৩৩ চৈত্র
ভারতচন্দ্র
শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ
গত বছর দু-তিন ধরে বাংলাদেশের মফস্বলে নানা সাহিত্য-সমিতির বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়মিত নিমন্ত্রিত হই। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ যে আমাকে তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন, এ আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কারণ এই সূত্রে প্রমাণ হয় যে, আমার পক্ষে বঙ্গসাহিত্যের চর্চাটা বৃথা কাজ বলে গণ্য হয় নি। ভারতচন্দ্র বলেছেন–
যার কর্ম তারে সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে
বাঙালি জাতি যে মনে করে লেখা জিনিসটি আমার সাজে, এ কি আমার পক্ষে কম শ্লাঘার কথা?
কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ অধিকাংশ নিমন্ত্রণই আমি রক্ষা করতে পারি নে। ইংরেজিতে যাকে বলে The spirit is willing, but the flesh is weak, আমার বর্তমান অবস্থা হয়েছে তাই। সমস্ত বাংলাদেশময় ছুটে বেড়াবার মত আমার শরীরে বলও নেই, স্বাস্থ্যও নেই। যে স্বল্পপরিমাণ শারীরিক বল ও স্বাস্থ্যের মূলধন নিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করি, কালক্রমে তার অনেকটাই ক্ষয় হয়েছে; যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকু কৃপণের ধনের মত সামলে ও আগলে রাখতে হয়। তৎসত্ত্বেও শান্তিপুরের নিমন্ত্রণ আমি অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এর কারণ নিবেদন করছি।
প্রথমতঃ, একটি চিরস্মরণীয় লেখক সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, এবং সেসব কথা শোনবার অনুকূল শ্রোতার অভাব, আমার বিশ্বাস, এ নগরীতে হবে না। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত সূত্রে আমার নিজের সম্বন্ধেও দু-একটি ব্যক্তিগত কথা বলতেও আমি বাধ্য হব। সমালোচকেরা যখন সাহিত্য-সমালোচনা করতে বসে কোনো সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও চরিত্রের আলোচনা শুরু করেন, তখন প্রায়ই তা আক্ষেপের বিষয় হয়; কারণ কোনো লেখকের লেখা থেকে তার জীবনচরিত উদ্ধার করা যায় না। তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা-প্রণোদিত সমালোচকদের কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করাও আমি এ যুগের সাহিত্যিকদের কর্তব্য বলে মনে করি। যুগধর্মানুসারে একালে সাহিত্য-সমালোচনাও একরকম বিজ্ঞান। এবং তার জন্য নাকি লোকের ঘরের খবর জানা চাই।
২.
সম্প্রতি কোনো সমালোচক আবিষ্কার করেছেন যে, আমি হচ্ছি এ যুগের ভারতচন্দ্র, অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বংশধর। এমন কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নিন্দা করা কি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করা, তা ঠিক বোঝা গেল না। যদি আমার নিন্দা হয় তত ভারতচন্দ্র সে নিন্দার ভাগী হতে পারেন না। আর যদি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা হয় তো সে প্রশংসার উত্তরাধিকারী আমি নই। সম্ভবতঃ সমালোচকের মুখে ভারতচন্দ্রের স্তুতি ব্যাজস্তুতি, অর্থাৎ বর্ণচোরা নিন্দা মাত্র। এখন এ স্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, যে-জাতীয় নিন্দা-প্রশংসার আমরা অধিকারী ভারতচন্দ্র সে-জাতীয় নিন্দা-প্রশংসার বহিভূত।
ভারতচন্দ্র আজ থেকে প্রায় এক শ আশি বৎসর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, অথচ আজও আমরা তার নাম ভুলি নি, তার রচিত কাব্যও ভুলি নি, এমন কি তার রচিত সাহিত্য নিয়ে আজও আমরা উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছি।
অপর পক্ষে আজ থেকে এক শ আশি বৎসর পরে বাংলার ক’জন সাহিত্যিকের নাম বাঙালি জাতি মনে করে রাখবে? আমার বিশ্বাস, বর্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এতদ্ব্যতীত আরও দু-এক জনের নাম হয়তো আগামীকালের বঙ্গসাহিত্যের কোনো ইতিহাসের ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে; বাদবাকি আমরা সব জলবুদবুদ, জলে মিশিয়ে যাব।
আর-একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গত এক শ আশি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সভ্যতার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশ এখন ইংরেজের রাজ্য; আমাদের কর্মজীবন এখন ইংরেজ-রাজের প্রবর্তিত মার্গ অবলম্বন করেছে। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমাদের মনোজগতেও বিপ্লব ঘটেছে। অথচ দেশের লোকের জীবনে ও মনে এই খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র চিরজীবী হয়ে রয়েছেন। এরই নাম সাহিত্যে অমরতা। আর এক্ষেত্রে সমালোচনার কার্য লৌকিক নিন্দা-প্রশংসা নয়, এই অমরতার কারণ আবিষ্কার করা; কিন্তু তা করতে হলে মনকে রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত করতে হয়। অথচ দুর্বিনীত সাহিত্যে রাগই পুরুষের লক্ষণ বলে গণ্য।
৩.
সকল দেশের সকল সাহিত্যেরই এমন দু-একটি সাহিত্যিক থাকেন, যাঁরা লোকমতে যুগপৎ বড় লেখক ও দুষ্ট লেখক বলে গণ্য। উদাহরণ স্বরূপ ইতালিদেশের মাকিয়াভেলির নাম করা যেতে পারে। মাকিয়াভেলির The Prince সাহিত্য হিসেবে ও রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে যে ইউরোপীয় সাহিত্যের একখানি অপূর্ব ও অতুলনীয় গ্রন্থ, এ কথা ইউরোপের কোনো মনীষী অস্বীকার করেন না, অথচ মাকিয়াভেলি নামটি গাল হিসাবেই প্রসিদ্ধ।।
আমাদের ভাষার ক্ষুদ্র প্রাণ সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের নামটিও উক্ত পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। ভারতচন্দ্রের এ দুর্নামের মূলে কতটা সত্য আছে, সেটা এখন যাচিয়ে দেখা দরকার। কারণ কুসংস্কার মাত্রই কালক্রমে সমাজে সুসংস্কার বলে গণ্য হয়। সাহিত্যসমাজেও অনেক সময়ে উক্ত হিসেবে কু সু এবং সুকু হয়ে উঠে।
ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয়ে এ যুগের সাহিত্যিকদের কতটা মিল আছে সে বিষয়ে ঈষং লক্ষ্য করলেই ভারতচন্দ্রের যথার্থ রূপ ফুটে উঠবে।
প্রথমে তার জীবনচরিত আলোচনা করা যাক। বলা বাহুল্য, তার জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা নেই। তবে তিনি নিজমুখেই তার জীবনের দুটি-চারটি মোটা ঘটনা প্রকাশ করেছেন।
আমার অকরুণ সমালোচক বলেছেন যে, ভারতচন্দ্র ও আমি—আমরা উভয়েই—উচ্চব্রাহ্মণবংশে উপরন্তু ভূসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। ভারতচন্দ্রের সম্বন্ধে ঘটনা যে তাই, তিনি তা গোপন করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন যে—
ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তার অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।
এখন জিজ্ঞাসা করি, কোনো লেখকের লেখা বিচার করতে বসে তার কুলের পরিচয় নেবার ও দেবার সার্থকতা কি। বিশেষত, সে বিচারের উদ্দেশ্য যখন লেখককে অপদস্থ করা।
যদি পৃথিবীর এমন কোনো নিয়ম থাকত যে, লেখক উচ্চব্রাহ্মণবংশীয় হলেই তাকে নিম্নশ্রেণীর লেখক হতে হবে, তাহলে সমালোচক অবশ্য কুলজ্ঞ হতে বাধ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করাটা তত সাহিত্যসমাজে লজ্জার বিষয় নয়। ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু কবি তত জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং তার জন্য তাদের ইতিপূর্বে কেউ তো হীনচক্ষে দেখে নি।
শুনতে পাই, ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথে Non-Brahmin Movement নামক একটি ঘোর আন্দোলন চলছে, কিন্তু সে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে। আমি উক্ত আন্দোলনের পক্ষপাতী। কিন্তু উত্তরাপথের সাহিত্যক্ষেত্রেও যে ব্রাহ্মণনিগ্রহের জন্য কোনো দল বদ্ধপরিকর হয়েছে, এমন কথা আজও শুনি নি। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে স্বীকার করছি যে, আমিও সেই সম্প্রদায়ের লোক, যে সম্প্রদায়ের গায়ত্রীমন্ত্রে জন্মসুলভ অধিকার আছে। এ বংশে জন্মগ্রহণ করাটা এ যুগে অবশ্য গৌরবের কথা নয়, কিন্তু অগৌরবের কথাও তো নয়।
সম্ভবতঃ সমালোচকের মতে একে ব্রাহ্মণ তায় ভূসম্পন্ন হওয়াটা, একে। মনসা তায় ধুনোর গন্ধের সংযোগের তুল্য। ভারতচন্দ্র এ-জাতীয় সমালোচকের মতে যতটা অবজ্ঞার পাত্র, কবিকঙ্কণ বোধ হয় ততটা নন। কারণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার চণ্ডীকাব্যের আরম্ভে এই বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন যে–
দামুন্যায় চাষ চষি।
কিন্তু চাষ না চষলে যে বড় লেখক হওয়া যায় না, সাহিত্যজগতে তারও কোনো প্রমাণ নেই।কারণ ধানের চাষ পৃথিবীতে একমাত্র চাষ নয়, মনের চাষ বলেও একরকম চাষ আছে, আর সেই চাষেরই ফসল হচ্ছে সাহিত্য। অন্ততঃ এতদিন তাই ছিল।
আমার মনে হয় যে, ভারতচন্দ্রের জাতি ও সম্পত্তির উপর কটাক্ষ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঙ্গিতে এই কথাটা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, এরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করবার জন্যই সাহিত্যচর্চা তার পক্ষে বিলাসের একটি অঙ্গমাত্র ছিল। সুতরাং তিনি যে সাহিত্য রচনা করেছেন, সে হচ্ছে বিলাসী সমাজের প্রিয়। আজীবন বিলাসের মধ্যে লালিতপালিত হলে লোকে যে-সরস্বতীর সেবা করে তার নাম নাকি দুষ্ট সরস্বতী। লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন সাহিত্যজগতে যে অনর্থ ঘটায়, এমন কথা অপরের মুখেও, অপর কোনো কবির সম্বন্ধেও শুনেছি। সুতরাং ভারতচন্দ্রের জীবন কতটা বিলাসবৈভবপূর্ণ ছিল, তারও কিঞ্চিং পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।
৪.
সমালোচকরা আবিষ্কার করেছেন যে, আমার জীবন হচ্ছে একটি ট্রাজেডি। এক হিসেবে মানুষমাত্রেরই জীবন একটা ট্রাজেডি, এবং আমি অবশ্য সাধারণ মানবধর্মবজিত নই। কিন্তু কি কারণে আমার জীবন অনন্যসাধারণ ট্রাজেডি সে কথাটা তারা প্রকাশ করে বলেন নি, বোধ হয় এই কারণে যে, আমার জীবন সুখময় কি দুঃখময়, তা অপরের কাছে সম্পূর্ণ অবিদিত। আর আমার জীবনের যে-পরিচয় সকলেই পান, তাকে ঠিক ট্রাজেডি বলা চলে না। আমার মাথার উপর চাল আছে, আর সে চালে খড় আছে, আমার ঘরে ক্ষুধার চাইতে বেশি অন্নের সংস্থান আছে, উপরন্তু আমার পরিধানের বস্ত্র আছে, ইংরেজি বাংলা দু রকমেরই। এর বেশি সামাজিক লোকে আর কি চায়? আর যে progressএর আমরা জাতকে জাত অনুরক্ত ভক্ত হয় পড়েছি, তারই বা চরম পরিণতি কি? সকলের পেটে ভাত ও পরনে কাপড়ই এ যুগে মানবসভ্যতার ঢরম আদর্শ নয় কি? সম্ভবতঃ আমার গুণগ্রাহী সমালোচকদের বক্তব্য হচ্ছে, আমার সাংসারিক জীবন নয়, সাহিত্যিক জীবনই একটা মস্ত ট্রাজেডি; অর্থাৎ আমার সাংসারিক জীবন মহা ট্রাজেডি হলে আমার সাহিত্যিক জীবন এত বড় প্রহসন হত না।
সে যাই হোক, ও বিষয়ে ভারতচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোনো মিল নেই। ভারতচন্দ্রের সাংসারিক জীবন ছিল সত্যই একটি অসাধারণ ট্রাজেডি। সংক্ষেপে ভারতচন্দ্রের জীবনের মূল ঘটনাগুলি বিবৃত করছি, তার থেকেই প্রমাণ পাবেন যে, তার জীবনের তুল্য ট্রাজেডি বাংলার কোনো সাহিত্যিকেরই জীবনে নেই; এমনকি তাদেরও নেই যাঁদের সাহিত্যিক জীবন হচ্ছে একেবারে ডিভাইন কমেডি।
ভারতচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে আমি কোনরূপ গবেষণা করি নি, কারণ এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল যে, ভগবান আমাকে কোনো বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য এ পৃথিবীতে পাঠান নি। সুতরাং পরের মুখের কথার উপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে।
১৩০২ শতাব্দে দ্বারকানাথ বসু নামক জনৈক ব্যক্তি ‘কবির জীবনী সম্বলিত’ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। এই অখ্যাতনামা প্রকাশকের প্রস্তাবনা হতে আমি ভারতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহ করেছি। আমার বিশ্বাস, বসুমহাশয়ের দত্ত বিবরণ সত্য। কারণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্ৰীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তার গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে প্রায় একই গল্প বলেছেন; শুধু বসুমহাশয়ের বঙ্গাব্দ সেনমহাশয়ের হাতে খৃস্টাব্দে পরিণত হয়েছে, এই তফাত।
৫.
১৭১২ খৃস্টাব্দে ভারতচন্দ্র হুগলি জেলার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূরসুট পরগনার অধিপতি ছিলেন। বর্ধমানাধিপতির সঙ্গে বিবাদে তিনি সর্বস্বান্ত হন।
ভারতচন্দ্রের বয়স তখন এগারো বছর। এই অল্প বয়সেই তিনি বিদ্যাভ্যাসার্থ লালায়িত হন। পিতার বর্তমান নিঃস্ব অবস্থায় যথারীতি বিদ্যাশিক্ষার অসুবিধা হওয়ায় তিনি ‘পলায়ন পূর্বক’ মাতুলালয়ে গমন করেন; এবং তথায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান অতি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করেন। উভয় বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করে তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে পেঁড়োয় ফিরে আসেন। অতঃপর তার বিবাহ হয়।
অর্থকরী পারস্য ভাষা শিক্ষা না করে অনর্থকরী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের দ্বারা ভংসিত হয়ে তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করেন।
তার পর দেবানন্দপুর গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র মুনশির আশ্রয়ে থেকে তিনি অতিপরিশ্রমপূর্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাভ্যাসের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। দিনে স্বহস্তে একবার মাত্র রন্ধন করে তাই দু বেলা আহার করতেন। অনেক সময়ে বেগুনপোড়া ছাড়া আর-কিছু তার কপালে জুটত না। এই সময়ে ভারতচন্দ্ৰ কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। পারস্য ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করে তিনি বিশ বৎসর বয়সে বাড়ি ফেরেন। তার আত্মীয়স্বজনেরা তখন তার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ভারতচন্দ্রকে তাদের মোক্তার নিযুক্ত করে বর্ধমানের রাজধানীতে তাদের হয়ে দরবার করতে পাঠান। রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে ভারতচন্দ্র বর্ধমানে কারারুদ্ধ হন। তার পর কারাধ্যক্ষের কৃপায় জেল থেকে পালিয়ে কটুকে মারহাট্টাদের সুবেদার শিবভট্টের আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন। পরে তিনি এক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের সঙ্গে বাস করে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয় পাঠ করেন। ফলে তিনি ভক্তিমান্ বৈষ্ণব হয়ে গেরুয়া বসন ধারণ করে সদাসর্বদা ধর্মচিন্তায় কালাতিপাত করিতেন। তার পর বৃন্দাবনধাম-দর্শন-মানসে তিনি শ্রীক্ষেত্র হতে পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথিমধ্যে খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে তাঁর শ্যালীপতি ভ্রাতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারই অনুরোধে ভারতচন্দ্র আবার সংসারী হতে স্বীকৃত হন, এবং অর্থোপার্জনের জন্য ফরাসডাঙায় দুপ্লে সাহেবের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।
কিছুদিন পরে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র টাকা ধার করবার জন্য ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হন, এবং তারই অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনেয় নিজের সভাস নিযুক্ত করেন।
এই সময়ে তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল শুনে খুশি হয়ে ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন এবং সেখানে বাড়ি তৈরি করবার জন্য এককালীন এক শ টাকা দান করেন। এই গ্রামেই তিনি ৪৮ বৎসর বয়েসে ভবলীলা সাঙ্গ করেন।
তার শেষবয়েসের কটা দিন যে কি ভাবে কেটেছিল, তার পরিচয় তার রচিত নাগাষ্টকে পাওয়া যায়। আমি উক্ত অষ্টকের তিনটি মাত্র চৌপদী এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি–
গতে রাজ্যে কার্যে কুলবিহিতবীর্যে পরিচিতে
ভবেদ্দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে কথমপি।
স্থিতং মূলাজোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগে হরি হরি।
বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া
কৃতা সেবা দেবাদপিকমিতি মত্মাপ্যহরহঃ।
কৃতাবাটী গঙ্গাভজনপরিপাটী পুটকিতা
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগে হরি হরি।
পিতা বৃদ্ধ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী
হতাশাদাপাদ্যাশ্চকিতমনসো বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শত্নং ধনমপি চ বং চিরচিত
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগগা হরি হরি।
৬
যিনি রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করে এগারো বৎসর বয়সে পরভাগগ্যাপজীবী হতে বাধ্য হন, যিনি এগারো থেকে বিশ বৎসর পর্যন্ত পরের আশ্রয়ে পরামভোঙ্গনে জীবনধারণ করে বিদ্যা অর্জন করেন, তার পর আত্মীয়স্বজনের জন্য ওকালতি করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন, তার পর জেল থেকে পালিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে কটুকে গিয়ে মারহাট্টাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, তার পর শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চা করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তার পর আবার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবার জন্য প্রথমে দুপ্লে সাহেবের দেওয়ানের, পরে কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট আশ্রয় পান, আর তথায় মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনের চাকর হয়ে কাব্যরচনা করেন, এবং শেষকালে গঙ্গাতীরে বাস করতে গিয়ে আবার বর্ধমান-রাজার কর্মচারিগুণ কর্তৃক নানারকম উৎপীড়িত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি যে কতটা বিলাসের মধ্যে লালিতপালিত হয়েছিলেন তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন।
এরূপ জীবন কল্পনা করতেও আমাদের আতঙ্ক হয়। আমাদের জীবন আজও অবশ্য হ্রাসবৃদ্ধির নিয়মের অধীন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত অবস্থার বিপর্যয় আজ কারও কপালে ঘটে না। ভারতচন্দ্রের জীবন দেশব্যাপী ভূমিকম্প ও ঝড়জলের ভিতর কেটে গেছে। সেকালের দেশের অবস্থা যদি কেউ জানতে চান, তাহলে তিনি অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনা পড় ন। সেকালে এ দেশের লোকের আরামও ছিল না, বিলাসী হবার সুযোগও ছিল না। ভারতচন্দ্র বলেছেন–
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।
সে যুগে দেশের কোনো লোকের হাতে ক্ষণের জন্য চাদ আসুক আর না আসুক, অনেকের ভাগ্যেই ক্ষণে হাতে দড়ি পড়ত। ভারতচন্দ্রের তুলনায় আমরা সকলেই আলালের ঘরের দুলাল, অর্থাৎ আমরা সকলেই কলের জল খাই, রেলগাড়িতে ঘোরাফেরা করি, পদব্রজে পুরী থেকে বৃন্দাবন তো দূরের কথা, শ্যামবাজার থেকে কালীঘাটে যেতে প্রস্তুত নই; এবং চল্লিশ টাকা মাস-মাইনেয় কাব্য লেখা দূরে থাক্, অত কমে আমরা কেউ মাসিক পত্রের এডিটারি করতেও নারাজ। নিজেরা আরামে আছি বলে আমরা মনে করি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যারা কবিতা লিখতেন, তারা সব সঁতে হীরে ঘষতেন আর তাদের ঘরে রুইমাছ ও পালং শাক ভারে ভারে আসত।
৭.
এ হেন অবস্থায় পড়লে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মন বিষাক্ত ও রসনা কণ্টকিত হয়ে ওঠে, এবং বিলাসীর মন তো একেবারে জীবন্ম ত হয়ে পড়ে। এখন দেখা যাক, সাংসারিক জীবনের এত দুঃখকষ্ট ভোগ করে ভারতচন্দ্রের মনের আলো নিবে গিয়েছিল, না, আরও জ্বলে উঠেছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে যে পতিনিন্দা করিয়েছেন, সেই নিন্দার ভিতরই আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাব। সেই নিন্দাবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি।।
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।।
পেটে অন্ন হেটে বস্তু জোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে।।
নানাশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে কত বলে বলিহারি তার।।
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদের প্রভু।
এই ব্যজনিন্দা হচ্ছে, ভারতচন্দ্রের আত্মকথা। ঐ কথা শুনে আমরা দুটি জিনিসের পরিচয় পাই : রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাস হয়েও তার দারিদ্র ঘোচে নি, এবং দারিদ্র্য তাকে নিরানন্দ করতে পারে নি, করেছিল শুধু প্রমোদের প্রভু। এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যাবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিকালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়। যে লোক ইউরোপে দ্বিতীয় শেক্সপীয়ার বলে গণ্য, সেই Cervantes সেভান্তেসের জীবন বিষম দুঃখময় ছিল, অথচ তার হাসিতে সাহিত্যজগৎ চিরআলোকিত। এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন বীরের হাসি। এ-জাতীয় হাসির ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পল্টনী বীরত্ব নয়, ব্যাবহারিক জীবনের সুখদুঃখকে অতিক্রম করবার ভিতর যে বীরত্ব আছে, তাই। এ হাসির মূলে কি আছে ভারতচন্দ্র নিজেই বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই–
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ।
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী।।
৮.
পূর্বেই বলেছি ভারতচন্দ্রের জীবনীর বিষয় বিশেষ কিছু জানা নেই। তার রচিত অন্নদামঙ্গল, মানসিংহ, সত্যনারায়ণের পুঁথি প্রভৃতিতে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাই অবলম্বন করে এবং লোকমুখে তার সম্বন্ধে কিংবদন্তী শুনে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর যে জীবনচরিত লেখেন, সেই জীবনচরিত থেকেই তাঁর পরবর্তী লেখকেরা তাঁর জীবনের ইতিহাস গড়ে তুলেছেন। সেই ইতিহাসটি আপনাদের কাছে এইজন্য ধরে দিলুম যে, আপনারা সকলেই দেখতে পাবেন যে, তাঁর কাব্যের দোষগুণ তাঁর অসার চরিত্রের ফুল কিংবা ফল নয়, বরং ঠিক তার উলটো। তাঁর কাব্যের চরিত্র যাই হোক, তার নিজের চরিত্র ছিল অনন্যসাধারণ আত্মবশ। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর ঘোর দুঃখময় জীবনের ছায়া তার কাব্যের গায়ে পড়ে নি। ব্যাপারটির প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য। কারণ তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, মানুষের মন তার জীবনের বিকার মাত্র। বিশেষতঃ যারা অচেতচিত্ত, তাদের মনে এই ধারণা একেবারে বদ্ধমূল হয়েছে। তা যে হয়েছে তার প্রমাণ, এ যুগে ইউরোপে বহু কবি আবির্ভূত হয়েছেন, যারা শুধু নিজের সুখদুঃখের গান গেয়েছেন কখনো হেসে, কখনো কেঁদে। প্রথমপুরুষকে উত্তমপুবুষ গণ্যে তারই কথাই হয়েছে তাদের কাব্যের মাল ও মসলা। কিন্তু এদেরও এই স্ব বস্তুটি যে-ক্ষেত্রে অহং সে-ক্ষেত্রে তারা অকবি, আর যে-ক্ষেত্রে তা আত্মা সে-ক্ষেত্রে তারা কবি। অহং ও আত্মা যে। এক বস্তু নয়, সে কথা কি এদেশে বুঝিয়ে বলা দরকার? ভারতচন্দ্র ছোট হোন বড় হোন–জাতকবি, সুতরাং তার অহং এর পরিচয় তার কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ, আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত, এসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে। সুখের বিষয়, সংস্কৃত কবিদের জীবনচরিত আমাদের কাছে অবিদিত, নচেৎ সমালোচকদের হাতে তারাও নিস্তার পেতেন না।
৯.
আন্দাজ দশ-বারো বৎসর আগে আমি দারজিলিং শহরে একটি সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায়। একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি। পরে দেশে ফিরে সেই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করি। বলা বাহুল্য, প্রাক্-বৃটিশ যুগের, ভাষান্তরে নবাবি আমলের, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের নাম উহ্য রাখা চলে না। তাই উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যাসুন্দর নামক কাব্যের দোষগুণ বিচার করতে আমি বাধ্য হই। সে প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের অতিপ্রশংসাও নেই, অতি নিন্দাও নেই। এর কারণ নিন্দা-প্রশংসায় যারা সিদ্ধহস্ত, তাদের ও-বিষয়ে অতিক্রম করবার আমার প্রবৃত্তিও নেই, শক্তিও নেই। কারও পক্ষে অথবা বিপক্ষে জোর ওকালতি করা আমার সাধ্যের অতীত। প্রমাণ, আমি ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করেছি কিন্তু আদালতের পরীক্ষায় ফেল হয়েছি। ভারতচন্দ্র বলেছেন, উকিলের–
সবে গুণ, যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে।
সাহিত্যের আদালতে এ গুণের গুণগ্রাহীরা আমাকে নির্গুণ বলেই প্রচার করেছেন।
সে যাই হোক, উক্ত প্রবন্ধ থেকেই সাধু সাহিত্যাচার্যেরা ধরে নিয়েছেন যে, আমি আর ভারতচন্দ্র দু জনে হচ্ছি পরস্পরের মাসতুতো ভাই। আমি উক্ত ইংরেজি প্রবন্ধটি আজ আবার পড়ে দেখলুম, তাতে এমন একটিও কথা নেই যা আমি তুলে নিতে প্রস্তুত। সমালোচকদের স্থূলহস্তাবলেপের ভয়ে আমি আমার মতামতকে ডিগবাজি খাওয়াতে শিখি নি।
যা একবার ইংরেজিতে বলেছি, বাংলায় তার পুনরুক্তি করবার সার্থকতা নেই। শুধু তার একটি মত সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে দু-চার কথা বলতে চাই। সে কথাটি এই
Bharatcliandra, as a supreme literary craftsman, will ever remain a master to us writers of the Bengali language.
১০
আমি এখন লেখক হিসেবেই, পাঠক হিসেবে নয়, ভারতচন্দ্রের লেখার সম্বন্ধে আরও দু-চারটি কথা বলতে চাই। আমি যে একজন লেখক, সে কথা অবশ্য তারা স্বীকার করেন না, যারা আমার লেখা আদ্যোপান্ত পড়েছেন, এমন কি তার microscopic examination করেছেন। ভাগ্যিস আমাদের চোখের জ্যোতি এক্স-রে নয়, তা হলে আমরা চার পাশে শুধু নরকঙ্কাল দেখতে পেতুম। কিন্তু আপনারা যে আমাকে লেখক বলে গণ্য করেন, তার প্রমাণ, আপনারা আমাকে এই উচ্চ আসন দিয়েছেন, আমি বক্তা বলে নয়, লেখক বলে।
ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের আরম্ভেই একবার বলেছেন–
কৃষ্ণচন্দ্রভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।
তার পর আবার বলেছেন–
নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাসে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।
কথা যুগপৎ সরল করে ও সরস করে বলতে চায় শুধু সাহিত্যিকরা; কারণ কোনো সাহিত্যিকই অসরস ও অসরল কথা ইচ্ছে করে বলে না; তবে কারও কারও স্বভাবের দোষে বিরস ও কুটিল কথা মুখ থেকে অনর্গল বেরোয়।
আমি এ কথা স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, আমি সরল ও সরস ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছি। তবে তাতে অকৃতকার্য হয়েছি কি না, তার বিচারক আমি নই, সাহিত্যসমাজ।
ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি। এর কারণ আমিও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করেছি। আমি পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসি, আর পনেরো বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর ছাড়ি। এই দেশই আমার মুখে ভাষা দিয়েছে, অর্থাৎ এ দেশে আমি যখন আসি তখন ছিলুম আধআধভাষী বাঙাল, আর স্পষ্টভাষী বাঙালি হয়ে এ দেশ ত্যাগ করি। আমার লেখার ভিতর যদি সরলতা ও সরসতা থাকে তো সে দুটি গুণ এই নদীয়া জিলার প্রসাদে লাভ করেছি। ফলে বাংলায় যদি এমন কোনো সাহিত্যিক থাকেন, যিনি–
কহিলে সরস কথা বিরস বাখানে,
তাকে দূর থেকে নমস্কার করি মনে মনে এই কথা বলে যে, তোমার হাতযশ আর আমার কপাল।
১১.
ভারতচন্দ্রের লেখার ভিতর কোন্ কোন্ গুণের আমরা সাক্ষাৎ লাভ করব তার সন্ধান তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন যে–
পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।
ভারতচন্দ্র যা পড়েছিলেন তা যে লিখতে পারতেন, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই, কারণ নিত্য দেখতে পাই হাজার হাজার লোক তা করতে পারে। এই বাংলাদেশে প্রতি বৎসর স্কুলকলেজের ছেলেরা যখন পরীক্ষা দেয় তখন তারা যেই মত পড়িয়াছে সেই মত লেখা ছাড়া আর কি করে? আর যে যত বেশি পড়া দিতে পারে সে তত বেশি মার্ক পায়। তবে সেসব লেখা যে ‘বুঝিবারে ভারি’ তা তিনিই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন, যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে কখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিদ্যার পরীক্ষক হয়েছেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, ও-জাতীয় লেখার ভিতর প্রসাদগুণও নেই, রসও নেই, আছে শুধু বইপড়া মুখস্থ পাণ্ডিত্য। আশা করি, বাঙালি জাতি কস্মিকালেও বিলেতি ‘বিদ্যাভ্যাসাৎ’ এতদূর জড়বুদ্ধি হয়ে উঠবে না যে, উক্ত জাতীয় লেখাকে সাহিত্য বলে মাথায় তুলে নৃত্য করবে। ভারতচন্দ্র কি পড়েছিলেন ও ছিলেন জানেন?–
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক।।
পুরাণ-আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
কিন্তু তিনি যেই মত পড়েছিলেন, সেই মত লেখেন নি কেন, তাই বুঝলে সাহিত্যের ধর্ম যে কি, সকলের কাছেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
এ যুগে আমরা কোনো কবির জজ কিংবা উকিলকে ক্রিটিক বলে গণ্য করি নে, সাহিত্যসমাজের পাহারাওয়ালাদের তো নয়ই। তাকেই আমরা যথার্থ সমালোচক বলে স্বীকার করি, যিনি সাহিত্যরসের যথার্থ রসিক। এ জাতীয় রসগ্রাহীরা জানেন যে, সাহিত্যের রস এক নয়, বহু, এবং বিচিত্র। সুতরাং কোন্ লেখকের লেখায় কোন্ বিশেষ রস বা বিশেষ গুণ ফুটে উঠেছে তাই যিনি ধরতে পারেন ও পাঁচজনের কাছে ধরে দিতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ক্রিটিক।
১২.
এখন, ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রসাদগুণ যে অপূর্ব, এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, সে-গুণ সম্বন্ধে কোনো চক্ষুষ্মন্ বাঙালির পক্ষে অন্ধ হওয়া অসম্ভব। এখন, এই সর্ব-আলংকারিক-পূজিত গুণটি কি। যে লেখা সর্বসাধারণের কাছে সহজবোধ্য সেই লেখাই কি প্রসাদগুণে গুণান্বিত? তা যদি হত, তা হলে কালিদাসের কবিতার চাইতে মল্লিনাথের টীকার প্রসাদগুণ ঢের বেশি হত। তা যে নয় তা সকলেই জানে। প্রসাদগুণ হচ্ছে ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ। ভারতচন্দ্রের হাতে বঙ্গসরস্বতী একেবার ‘তন্বীশ্যামা শিখরদশনা রূপ ধারণ করেছেন। যার অন্তরে বঙ্গভাষা এই প্রাণবন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ লাভ করেছে, ঠার যে কবিপ্রতিভা ছিল, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষাকে শাপমুক্ত করা যদি তার একমাত্র কীর্তি হত তা হলেও আমরা বাঙালি লেখকেরা তাঁকে আমাদের গুরু বলে স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা করতুম না। অমন সরল ও তরল ভাষা তার পূর্বে আর কেউ লিখেছেন বলে আমি জানি নে। আর আমি অপর কোনো সাহিত্য জানি আর না-জানি, বাংলা সাহিত্য অল্পবিস্তর জানি।
আমি পূর্বোক্ত ইংরেজি প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষার মহা গুণকীর্তন করি, কিন্তু সে ভুল করে। সেকালে আমার চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। এখন দেখছি উক্ত পদাবলীর ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা নয়। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুখে রূপান্তরিত হয়েই চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা যে তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে, সে বিষয়ে আমি এখন নিঃসন্দেহ। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের হিস্টরি লেখা হয়েছে, কিন্তু এখনও সে সাহিত্যের জিয়োগ্রাফি লেখা হয় নি। যখন সে জিয়োগ্রাফি রচিত হবে তখন সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন যে, ভারতচন্দ্রের এ উক্তি সত্য যে, নবদ্বীপ সেকালে ছিল—
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ।
আমি বলেছি যে, প্রসাদগুণ ভাষার গুণ, কিন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে, ভাষা ছাড়া ভাব নেই। নীরব কবিদের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি নে। যা আমরা ভাষার গুণ বলি তা হচ্ছে মনের গুণেরই প্রকাশ মাত্র। অপ্রসন্ন অর্থাৎ ঘোলাটে মন থেকে প্রসন্ন ভাষা আবিভূত হতে পারে না। সুতরাং প্রসাদগুণ হচ্ছে আসলে মনেরই গুণ, ও-বস্তু হচ্ছে মনের অলোক।
১৩
ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন যে, তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ থাকবে ও ত হবে। রসাল। এ দুই বিষয়েই তার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। গোল তো এইখানেই। যে রস তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ রস সে রস এ যুগে অস্পৃশ্য। কেননা তা হচ্ছে আদিরস। উক্ত রসের শারীরক ভাষ্য এ যুগের কাব্যে আর চলে না, চলে শুধু দেহতত্ত্ব নামক উপবিজ্ঞানে।
সাদা কথায় ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীল। তার গোটা কাব্য অশ্লীল না থোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তা যে অশ্লীল তা স্বয়ং ভারতচন্দ্রও জানতেন, কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীল অঙ্গসকল তিনি নানাবিধ উপমা অলংকার ও সাধুভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।
এস্থলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তার পূর্ববর্তী বাংলা ও সংস্কৃত কবিরা কি খুব শ্লীল? রামপ্রসাদ অনেকের কাছে মহা সাধু কবি বলে গণ্য। গানরচয়িতা রামপ্রসাদ নিষ্কলুষ কবি, কিন্তু বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা রামপ্রসাদও কি তাই? চণ্ডীদাস মহাকবি, কিন্তু তার রচিত কৃষ্ণকীর্তন কি বিদ্যাসুন্দরের চাইতেও সুরুচিসম্পন্ন? এ দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই মাত্র কি না যে, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা আবৃত ও কৃষ্ণকীর্তনের অনাবৃত? আমি ভারতচন্দ্রের কাব্যের এ কলঙ্কমোচন করতে চাই নে, কেননা তা করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্য একা ভারতচন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি? এর প্রথম কারণ, ভারতচন্দ্রের কাব্য যত সুপরিচিত অপর কারও তত নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের আছে শুধু nature। ভারতচন্দ্র যা দিয়ে তা ঢাকা দিতে গিয়েছিলেন তাতেই তা ফুটে উঠেছে। তার ছন্দ ও অলংকারের প্রসাদেই তাঁর কথা কারও চোখ-কান এড়িয়ে যায় না। পাঠকের পক্ষে ও-জিনিস উপেক্ষা করবার পথ তিনি রাখেন নি। তবে একশ্রেণীর পাঠক আছে যাদের কাছে ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা ততটা চোখে পড়ে না যতটা পড়ে তার আর্ট। তার পর ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গম্ভীর নয়, সহাস্য।
১৪
ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে এ রসের নাম আছে, কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে এ রসের বিশেষ স্থান নেই। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকদের রসালাপ শুনে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু সে তাদের কথায় হাস্যরসের একান্ত অভাব দেখে। ও হচ্ছে পেটের দায়ে রসিকতা।
বাংলার প্রাচীন কবিরা কেউ এ রসে বঞ্চিত নন। শুধু ভারতচন্দ্রের লেখায় এটি বিশেষ করে ফুটেছে। ভারতচন্দ্র এ কারণেও বহু সাধু ব্যক্তিদের কাছে অপ্রিয়। হাস্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিস্টফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিসটেই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহিভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।
ভারতচন্দ্রের কাব্য যে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট সে কথা তো সকলেই জানেন, কিন্তু তার হাসিও নাকি জঘন্য। সুন্দরের যখন রাজার সুমুখে বিচার হয় তখন তিনি বীরসিংহ রায়কে যেসব কথা বলেছিলেন তা শুনে জনৈক সমালোচকমহাশয় বলেছিলেন যে, শ্বশুরের সঙ্গে এহেন ইয়ারকি কোন সমাজের সুরীতি? আমিও জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সমালোচনা কোন্ সাহিত্যসমাজের সুরীতি? এর নাম ছেলেমি না জ্যাঠামি? তার নারীগণের পতিনিন্দাও দেখতে পাই অনেকের কাছে নিতান্ত অসহ্য। সে নিন্দার অশ্লীলতা বাদ দিয়ে তার বিক্রপেই নাকি পুরুষের প্রাণে ব্যথা লাগে। নারীর মুখে পতিনিন্দার সাক্ষাৎ তো ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী অন্যান্য কবির কাব্যেও পাই। এর থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, বঙ্গদেশের স্ত্রীজাতির মুখে পতিনিন্দা এষে ধর্মঃ সনাতনঃ। এস্থলে পুরুষজাতির কিং কর্তব্য? হাসা না কঁদা? বোধ হয় কঁদা, নচেৎ ভারতের হাসিতে আপত্তি কি। আমি উক্তজাতীয় স্বামী-দেবতাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, দেবতার চোখে পলকও পড়ে না, জলও পড়ে না। আমাদের দেবদেবীর পুরাণকল্পিত চরিত্র, অর্থাৎ স্বর্গের রূপকথা, নিয়ে ভারতচন্দ্র পরিহাস করেছেন। এও নাকি তার একটি মহা অপরাধ। এ যুগের ইংরেজিশিক্ষিতসম্প্রদায় উক্ত রূপকথায় কি এতই আস্থাবান যে, উক্ত পরিহাস তাদের অসহ? ভারত-সমালোচনার যে ক’টি নমুনা দিলুম তাই থেকেই দেখতে পাবেন যে, অনেক সমালোচক কোন্ রসে একান্ত বঞ্চিত। আশা করি, যে হাসতে জানে না সেই যে সাধুপুরুষ ও যে হাসাতে পারে সেই যে ইতর, এহেন অদ্ভুত ধারণা এ দেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংসতা মনে করি।
আমি আর-একটা কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করেই এ যাত্রা ক্ষান্ত হব। এ দেশে ইংরেজের শুভাগমনের পূর্বে বাংলাদেশ বলে যে একটা দেশ ছিল, আর সে দেশে যে মানুষ ছিল, আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল, আর সে ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হত, এই সত্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এই নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এ সত্য বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ, যেহেতু আমাদের শিক্ষাগুরুদের মতে বাঙালি জাতির জন্মতারিখ হচ্ছে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দ।
সর্বশেষে আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, সে প্রার্থনা ভারতচন্দ্রের কথাতেই করি। আপনারা আমাকে এ সভায় কথা কইতে আদেশ করেছেন–
সেই আজ্ঞা অনুসরি কথা শেষে ভয় করি
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখো দুষ্ট মত
সারি দিবা এই নিবেদন।
১৩৩৫ শ্রাবণ
মহাভারত ও গীতা
দেশপূজ্য ও লোকমান্য স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একখানি বিরাট ভাষ্য রচনা করেছেন, এবং মহাত্মা তিলকের অনুরোধে স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সে গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন।(১) সে ভাষ্য যে কত বিরাট তার ইয়ত্তা সকলে এই থেকেই করতে পারবেন যে, গীতার সপ্ত শত শ্লোকের মর্ম প্রায় সপ্তবিংশতি সহস্র ছত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ভাষ্য এত বিশাল হবার কারণ এই যে, এতে বেদ উপনিষদ ব্রাহ্মণ নিরুক্ত ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ পুরাণ ইতিহাস কাব্য দর্শন প্রভৃতি সমগ্ৰ সংস্কৃত শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুবিচার করা হয়েছে। মাহাত্ম তিলক এ গ্রন্থে যে বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান, যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা যথার্থই অপূর্ব। সমগ্র মহাভারতের নৈলকষ্ঠীয় ভাষ্যও, আমার বিশ্বাস, পরিমাণে এর চাইতে ছোট। তাইতে মনে হয় যে, এ ভাষ্য মহাত্মা তিলক প্রাকৃতে না লিখে সংস্কৃতে লিখলেই ভালো করতেন। কারণ এ গ্রন্থের পারগামী হতে পারেন শুধু সর্বশাস্ত্রের পারগামী পণ্ডিতজনমাত্র, আমাদের মত সাধারণ লোক এ গ্রন্থে প্রবেশ করা মাত্রই বলতে বাধ্য হবে যে–
ন হি পারং প্রপশ্যামি গ্রন্থস্যাস্য কথঞ্চন।
সমুদ্রস্যাস্য মহতো ভুজাভ্যাং প্রতরন্নরঃ॥(২)
২.
মহাত্মা তিলক এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন কর্মযোগ। কেননা তিনি ঐ সুবিস্তৃত বিচারের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, গীত কর্মত্যাগের শিক্ষা দেয় না, শিক্ষা দেয় কর্মযোগের। আর যোগ মানে যে কর্মসু কৌশলং, এ কথা তো স্বয়ং বাসুদেব গোঁড়াতেই অর্জুনকে বলেছেন। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। নীলকণ্ঠ গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন এই ক’টি কথা বলে–
প্রণম্য ভগবৎপাদান্ শ্রীধরাদীংশ্চ সগ্গুরুন্
সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারভে।
নীলকণ্ঠ অতি সাদা ভাবে স্বকীয় ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে-কথা মুখ ফুটে বলেছেন, গীতার সকল টীকাকারই সে-কথা স্পষ্ট করে না বললেও চাপা দিতে পারেন না। সকলেই স্বসম্প্রদায় অনুসারে ও-গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। যিনি জ্ঞানমার্গের পথিক, তিনি গীতাকে জ্ঞানপ্রধান ও যিনি ভক্তিমার্গের পথিক, তিনি গীতাকে ভক্তি প্রধান শাস্ত্র হিসাবেই আবহমান কাল ব্যাখ্যা করে এসেছেন। মহাত্মা তিলক তার ভাষ্যে উক্ত কাব্য অথবা স্মৃতির পঞ্চদশখানি পূর্ব-টীকার যুগপৎ বিচার ও খণ্ডন করেছেন। উক্ত পনেরোখানিই যে স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারেই রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহাত্মা তিলকও স্বসম্প্রদায় অনুসারেই তার নুতন ব্যাখ্যা করেছেন। যদি জিজ্ঞাসা। করেন যে, মহাত্মা তিলক কোন্ সম্প্রদায়ের লোক? তার উত্তর, এ যুগে আমরা সকলেই যে সম্প্রদায়ের লোক, তিনিও সেই একই সম্প্রদায়ের লোক। এ যুগ জ্ঞানের যুগ নয়, বিজ্ঞানের যুগ; ভক্তির যুগ নয়, কর্মের যুগ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে, আমাদের জন্মভূমি হচ্ছে কর্মভূমি। ভারতবর্ষ পৌরাণিক যুগে মানুষের কর্মভূমি ছিল কিনা জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের এ যুগ যে ঘোরতর কর্মযুগ, সে বিষয়ে, আশা করি, শিক্ষিত সমাজে দ্বিমত নেই। এতদেশীয় ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক সকলেই, জীবনে না হোক মনে, doctrine of actionএর অতি ভক্ত। সন্ন্যাসী হবার লোভ আমাদের কারও নেই; যদি কারও থাকে তত সে একমাত্র পলিটিকাল সন্ন্যাসী হবার। বলা বাহুল্য যে, পলিটিক্স কর্মকাণ্ডের ব্যাপার, জ্ঞানকাণ্ডের নয়, ভক্তিকাণ্ডেরও নয়। সংসারের প্রতি বিরক্তি নয়, আত্যন্তিক অনুরক্তিই। পলিটিকসের মূল। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধান প্রভেদ এই কি নয় যে, সে দেশের লোক ‘অজরামরবৎ’ বিদ্যা ও অর্থের চর্চা করে, আর আমরা ‘গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা’ ধর্মচিন্তা করি। আমার কথা যে সত্য তার টাটকা প্রমাণ, মহাত্মা তিলকের একটি আজীবন পলিটিকাল সহকর্মী লাল। লাজপত রায় এই সেদিন সকলকে বলে গেলেন যে, হিন্দুধর্ম আসলে সন্ন্যাসের ধর্ম নয়, কর্মের ধর্ম; এবং সেই সঙ্গে আমাদের সকলকে কায়মনোবাক্যে কর্মে প্রবৃত্ত করবার জন্য গীতার মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করবার আদেশ দিয়ে গেলেন, বোধ হয় এই ভয়ে যে, মনোযোগ সহকারে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ করলে আমাদের কর্মপ্রবৃত্তি হয়তো নিস্তেজ হয়ে পড়তে পারে। এ ভয় অমূলক নয়।
৩.
ইংরেজের শিষ্য আমরা যেমন কর্মের উপাসক, শ্ৰীধরের শিষ্য নীলকণ্ঠও তেমনি ভক্তির উপাসক ছিলেন, তথাপি তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে–
ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী মতা।।
কর্মোপাস্তিজ্ঞানভেদৈঃ শাস্ত্র কাণ্ডত্ৰয়াত্মকম্।
অন্যে তূপাসনাকাণ্ডাতৃতীয়ো নাতিরিচ্যতে।।
তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি ত্বং নেদং যত্তদুপাসতে।
ইতি শ্রুত্যৈব বেদ্যস্য হ্যুপাস্যদন্যতেরিতা।।
ইয়মষ্টাদশাধ্যায়ী ক্ৰমাৎ ষটত্রিকেণ হি।
কর্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডত্ৰিতয়াত্ম৷ নিগদ্যতে।।
নীলকণ্ঠের এই সরল কথাই হচ্ছে সত্যকথা। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় যে কর্মকাণ্ডের, মধ্যের ছয় অধ্যায় যে ভক্তিকাণ্ডের, আর শেষ ছয় অধ্যায় যে জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত, এ রকম তিন অংশে সমান ও পরিপাটি ভাগবাটোয়ারার হিসেব আমরা না মানলেও, এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য যে, ও-শাস্ত্রে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি তিনই আছে। ও-গ্রন্থ একে তিন, কিন্তু তিনে এক নয়। গীতায় ও ত্ৰিকাণ্ডের রাসায়নিক যোগের ফলে কোনো একটি নবকাণ্ডের সৃষ্টি হয় নি। এই কারণে গীতার এমন কোনো এক ব্যাখ্যা হতে পারে না, যা চূড়ান্ত হিসেবে সর্বলোকগ্রাহ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে তিন রকম ব্যাখ্যারই সমান অবসর। আছে। গীতার অন্তরে নানারূপ ধাতু আছে। কোনো ভাষ্যকারই তাকে ব্যাখ্যার বলে তার মনোমত এক ধাতুতে পরিণত করতে কৃতকার্য হবেন না। তা সে ধাতু জ্ঞানের স্বর্ণ ই হোক আর কর্মের লৌহই হোক। পূর্বাচার্যের প্রধানতঃ গীতাভাষ্যে জ্ঞানভক্তিমার্গ ই অবলম্বন করেছিলেন; গীতার ধর্ম যে মুখ্যতঃ সন্ন্যাসের ধর্ম নয়, ভগবদ্গীতা যে অবধূত-গীতা ও অষ্টাবক্র-গীতার জ্যেষ্ঠ সহোদর নয়, এ কথা কিন্তু আজ আমরা জোর করে বলতে পারি।
গীতার মতকে কর্মযোগ বলবার আমাদের অবাধ অধিকার আছে। আর যুগধর্মানুসারে আমরা গীতা নিংড়ে সেই মতই বার করবার চেষ্টা করব। আর, এ প্রযত্ন মহাত্মা তিলকের তুল্য আর-কে করতে পারেন? এ যুগের তিনিই যে হচ্ছেন অদ্বিতীয় কর্মযোগী, এ সত্য আর শিক্ষিত অশিক্ষিত কোন্ ভারতবাসীর নিকট অবিদিত? এই গীতাভাষ্যও মহাত্মা তিলকের কর্মযোগের অদ্ভুত ক্রিয়া। জ্ঞানের তরফ থেকে শংকরের ভাষ্য যেমন একমেবাদ্বিতীয়ম্, কর্মের তরফ থেকে মহাত্মা তিলকের ভাষ্যও, আমার বিশ্বাস, তেমনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে থাকবে।
৪.
গীতা কর্মমার্গের, জ্ঞানমার্গের কি ভক্তিমার্গের শাস্ত্র, এ তর্ক হচ্ছে এ দেশের ও সেকালের। কিন্তু এই গ্রন্থ নিয়ে এ যুগে এক নূতন তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সে তর্কটা যে কি মহাত্মা তিলকের ভাষাতেই বিবৃত করছি–
গ্রন্থ কোথায় রচিত হইয়াছে, কে রচনা করিয়াছে, তাঁহার ভাষা কিরূপ–কাব্যদৃষ্টিতে তাহাতে কতট। মাধুর্য ও প্রসাদগুণ আছে, গ্রন্থের রচনা ব্যাকরণশুদ্ধ অথবা তাহাতে কতকগুলি আর্মপ্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন্ কোন্ মতের, স্থলের কিংবা ব্যক্তির উল্লেখ আছে, এইসকল ধরিয়া গ্রন্থের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে কি না…
এরূপ আলোচনাকে মহাত্মা তিলক বহিরঙ্গ পর্যালোচনা বলেন। এ আলোচনা আমরা অবশ্য বিলেত থেকে আমদানি করেছি।
পরন্তু, এক্ষণে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অনুকরণে এ দেশের আধুনিক বিদ্বানের। গীতার বাহাঙ্গেরই বিশেষ অনুশীলন করিতেছেন।
এরূপ আলোচনার প্রতি যারা আসক্ত তাদের প্রতি মহাত্মা তিলক যে আসক্ত নন, তার পরিচয় তিনি নিজ মুখেই দিয়েছেন। তিনি বলেন–
বাগদেবীর রহস্যজ্ঞ ও তাঁহার বহিরঙ্গ-সেবক, এই উভয়ের ভেদ দর্শন করিয়া মুরারি কবি এক সরস দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—
অব্ধিলঙ্ঘিত এব বানরভটৈঃ কিং ত্বস্য গম্ভীরতাম।
আপাতালনিমগ্নপীবরতনুর্জানাতি মন্থাচলঃ।।
আর গ্রন্থরহস্য মধ্যে মন্দার পর্বতের মত আপাতাল-নিমজ্জিত হওয়ারই নাম অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা। মুরারি কবির এই সরস উক্তিটি অবশ্য দেশি বিলেতি বহিরঙ্গ-সেবকদের কর্ণে একটু বিরস ঠেকবে। কিন্তু এ বিষয়ে যারা মদমত্ত জর্মান পাণ্ডিত্যের উল্লম্ফন নিরীক্ষণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে মুরারি কবির উক্তির পুনরুক্তি করবার লোভ সংবরণ করা কঠিন।
কাব্যের অন্তরঙ্গের সাধনা ও বহিরঙ্গের সেব। এ দুটি ক্রিয়ার ভিতর যে শুধু প্রভেদ আছে তাই নয়, এর একটি প্রযত্ন অপরটির অন্তরায়। কাব্যের ভিতর থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে বসলে দেখা যায় যে, তার কাব্যরস শুকিয়ে এসেছে আর তার ভিতর নিমজ্জিত ঐতিহাসিক উপলখণ্ড সব দন্তবিকাশ করে হেসে উঠেছে। আমাদের মত কাব্যরসিকরা কাব্যের সমগ্র রূপ দেখেই মোহিত হই, অপরপক্ষে পণ্ডিতরা কাব্যের রস জিনিসটিকে উপেক্ষা করেন, অন্ততঃ জর্মান পণ্ডিতরা কাব্যের সম্মুখীন হবামাত্র তাকে সম্বোধন করে বলেন–
মাইরি রস ঘুরে বোস্,
দাঁত দেখি তোর বয়েস কত।
এরই নাম স্কলারশিপ।
তবে এ রকম ঐতিহাসিক কৌতূহল যখন মানুষের মনে একবার জেগেছে, তখন কাব্যের ঐ বহিরঙ্গ-পর্যালোচনায় যোগ দেবার প্রবৃত্তি দমন করা অসম্ভব, বিশেষতঃ আধুনিক বিদ্বান ব্যক্তিদের পক্ষে। অন্যে পরে কা কথা, মহাত্মা তিলকও গীতার বহিরঙ্গ-পর্যালোচনার মায়া কাটাতে পারেন নি। তিনি তাঁর গীতাভাষ্যর পরিশিষ্টে অতি বিস্তৃত ভাবেই এই বাহবিচার করেছেন। এতে আমি মোটেই আশ্চর্য হই নি। এই পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে শাস্ত্ৰবিচারের এ দেশে রাজা ছিলেন স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর। আর মহাত্মা তিলক যে-পুরীকে পুণ্যপুনাপুর বলেন, সেই পুরীই হচ্ছে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের বাজধানী এবং সেই পুরীতেই এ দেশের যত বড় বড় ওরিয়েন্টালিস্ট অবতীর্ণ হয়েছেন। কর্মযোগে যতসব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উল্লেখ আছে সেসবই মহারাষ্ট্রীয়, একটিও বঙ্গদেশীয় নয়। স্বয়ং মহাত্মা তিলক হচ্ছেন এই বিলেতিদস্তুর-পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব এতই অসামান্য যে, পাশ্চাত্ত্য ওরিয়েন্টালিস্ট সমাজেও তিনি অতি উচ্চ আসন লাভ করেছেন।
পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা বিশেষ করে এই মহা প্রশ্ন তুলেছেন যে, মহাভারতে ভগবদগীতা প্রক্ষিপ্ত কি না। মহাত্মা তিলক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে-~
যে ব্যক্তি বর্তমান মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তিনিই বর্তমান গীতাও বিবৃত করিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তে তিনি অবশ্য উপনীত হয়েছেন বাহ্যপ্রমাণের বলে। কেননা তিনি এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে–
যাঁহারা বাহপ্রমাণকে মানেন না এবং নিজেরই সংশয়পিশাচকে অগ্ৰস্থান দেন, তাঁহাদের বিচারপদ্ধতি নিতান্ত অশাস্ত্রীয় সুতরাং অগ্রাহ। মহাত্মা তিলকের মতে
গীতাগ্রন্থ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক, এই ধারণা হইতেই এই সন্দেহ তো প্রথমে বাহির হয়।
আমি অবশ্য আচার্যের শিষ্য নই অর্থাৎ শংকরপন্থী বৈদান্তিক নই, এমন কি শংকরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলতেও আমার তিলমাত্র দ্বিধা নেই। তবুও মহাত্মা তিলকের সংগৃহীত বাহ্যপ্রমাণ আমার মনের সন্দেহ-পিশাচকে একেবারে বধ করতে পারে নি। এর প্রকৃত কারণ তিনিই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সন্দেহ নিরঙ্কুশ। আমি অবিদ্বান্, কিন্তু এতদ্দেশীয় ও আধুনিক। অতএব আমার মনেও অনেক বিষয়ে সন্দেহ আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। মনোজগতে ‘আধুনিক’ ও ‘সংশয়গ্রস্ত’ এ দুটি কথা পর্যায়শব্দ। যার মনে কোনোরূপ সংশয় নেই তার একালে জন্ম আসলে অকালে জন্ম; কারণ দেহে তিনি একেলে হলেও, মনে সেকেলে। এ প্রবন্ধে আমার সেই সন্দেহই আমি ব্যক্ত করতে চাই। পণ্ডিতের বিচারে অবশ্য যোগদান করবার অধিকার আমার নেই, কেননা পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রস্থানভূমি সন্দেহ হলেও নিঃসন্দিগ্ধ চুড়ান্ত সিদ্ধান্তই হচ্ছে তাদের গম্যস্থান। আর তারা অবলীলাক্রমেই সেখানে পৌঁছে যান। অপরপক্ষে আমি মহাভারতের নানা দেশ পর্যটন করে অবশেষে কোনো মানসিক রাজপুতনায় উপনীত হতে পারি নি। কারণ মহাভারতের ভিতর আমার পর্যটন শুধু ‘ভ্রমণ কারণ’। সুতরাং আমি অপণ্ডিত ও কাব্যরসিক বাঙালি হিসেবেই এ বিষয়ে একটু উচ্চবাচ্য করতে চাই।
৫.
আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে এই ‘প্রক্ষিপ্ত’ কথাটার চল করেছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা। এর একটি স্পষ্ট কারণ আছে। আঁদ্রে জিদ নামক জনৈক বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির উপর একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আরম্ভেই বলেছেন যে, গীতাঞ্জলির তনুতা দেখেই তিনি পুলকিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁর ভয় ছিল যে, যে দেশের মহাকাব্যের শ্লোকসংখ্যা হচ্ছে শত সহস্র, সে দেশের গীতিকাব্যের শ্লোক-সংখ্যা হবে অন্ততঃ এক সহস্র। আঁদ্রে জিদ সংস্কৃত জানেন না, যদি জানতেন তো তিনি মহাভারতের গোঁড়াতেই দেখতে পেতেন যে, লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা বলেছেন যে, বর্তমান মহাভারত হচ্ছে মূল মহাভারতের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ–
বিস্তীর্য্যেতন্মহজ্জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।
লোমহর্ষণ-পুত্রের এ কথা শুনলে জিদ সাহেবের যে শুধু লোমহর্ষণ হত তাই নয়, তিনি হয়তো মূৰ্ছিত হয়ে পড়তেন।
ইউরোপীয়েরা হোমারের ইলিয়াডের পরিমাণকেই মহাকাব্যের স্ট্যাণ্ডার্ড মাপ ধরে নিয়েছেন। কিন্তু গ্রীস নামক ক্ষুদ্র দেশের পরিমাণের সঙ্গে ভারতবর্ষ নামক মহাদেশের পরিমাণের তুলনা করলেই তারা বুঝতে পারবেন, কেন ইলিয়াডের মাপের সঙ্গে মহাভারতের মাপ মেলে না ও মিলতে পারে না। কিন্তু ভৌগোলিক হিসেব অনুসারেই যে কাব্যের দেহ সংকুচিত ও প্রসারিত হতে হবে, এ কথা তারা মানতে প্রস্তুত নন। তারা বলেন, মানচিত্রের সঙ্গে মন-চিত্রের কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। অতএব মহাভারত যখন কাব্য, তখন নৈসর্গিক নিয়মে তা এতাদৃশ মহাকায় হতে পারে না। কাব্যের কথা ছেড়ে দিলেও কাব্যরচয়িতা কবির তো দম বলে একটা জিনিস আছে। কোনো কবি এক দমে মহাভারতের অষ্টাদশ পূর্বের পাল্লা ছুটতে পারতেন না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, মহাভারতের মধ্যে অধিকাংশ শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত। এর উত্তর হচ্ছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ঐ কাব্য-নামেই ভুলেছেন। মহাভারত কব্যি নয়, মহাভারত হচ্ছে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া; সুতরাং এক লক্ষ শোকের অর্থাৎ দু লক্ষ ছত্রের বিশ্বকোষকে সংক্ষিপ্ত বললে আঁদ্রে জিদও কোনো আপত্তি করতে পারবেন না। এ গ্রন্থের নাম সংহিতা না হয়ে কাব্য কি করে হল, তার পরিচয় মহাভারতেই আছে। বেদব্যাসের মনে যখন এ গ্রন্থ জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি ব্রহ্মাকে বলেন যে, আমি মনে মনে একখানি কাব্য রচনা করেছি। সে কাব্যে কি কি জিনিস থাকবে, বেদব্যাসের মুখে তার ফর্দ শুনে স্বয়ং ব্রহ্মাও একটু চমকে ওঠেন ও থমকে যান, তার পর তিনি সসম্ভ্রমে বলেন যে, হে বেদব্যাস, তুমি যখন ও-গ্রন্থকে কাব্য বলতে চাও, তখন ওর নাম কাব্যই হবে, কেননা তুমি কখনো মিথ্যা কথা বল না। এর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান মহাভারতকে কাব্য বলা যায় কি না, সে বিষয়ে স্বয়ং ব্রহ্মারও সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিনি যে ও-গ্রন্থকে অবশেষে কাব্য বলতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তার কারণ মহাভারত একাধারে কাব্য আর এনসাইক্লোপিডিয়া; এবং এই দুই বস্তু একই গ্রন্থের অন্তর্ভুত হলেও মিলেমিশে একদম একাকার হয়ে যায় নি, মোটামুটি হিসেবে উভয়েই চিরকাল নিজ নিজ স্বাতন্ত্র রক্ষা করে আসছে। মহাভারতের যে অংশ আমাদের মত অবিদ্বান লোকেরা পড়ে। এবং উপভোগ করে সেই অংশ তার কাব্যাংশ; আর যে অংশ বিদ্বান্ লোকেরা কষ্টভোগ করে পর্যালোচনা করেন, সেই অংশই তার এনসাইক্লোপিডিয়ার অংশ। এ বিষয়ে বোধ হয় অপণ্ডিত মহলে কোনো মতভেদ নেই।
মহাভারতের এই যুগলরূপের প্রহেলিকাই হচ্ছে ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের শান্তিভঙ্গের মূল কারণ। এ হেঁয়ালির যাহোক-একটা হেস্তনেস্ত না করতে পারলে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের পণ্ডিতি মনের শান্তি ফিরে পাবেন না। এর জন্য তারা সকলে মিলে পাণ্ডিত্যের দাবাখেলা খেলতে শুরু করেছেন। এ খেলায় সকলেই সকলকে মাত করতে চান। আমি সে খেলার দর্শক হিসেবে দুটি-একটি উপর-চাল দিচ্ছি। সে চাল নেওয়া না-নেওয়া নির্ভর করছে খেলোয়াড়দের উপর। একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন যে, পণ্ডিতের দল ভারতবর্ষের অতীতকে প্রায় বেদখল করে নিয়েছে। বেদ এখন ফিললজির, ইতিহাস, নিউমিসম্যাটিক্সের এবং আর্ট আর্কিঅলজির অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছে অর্থাৎ একাধারে বিজ্ঞানের ও ইংরেজির। এ অবস্থায় মহাভারত যাতে বাংলা সাহিত্যের হাতছাড়া না হয়ে যায়, সে চেষ্টা আমাদের করা আবশ্যক। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিচারের হট্টগোলে যোগ দেওয়া। হেঁয়ালি সম্বন্ধে বাংলায় একটা কথা আছে যে–
মূর্খেতে বুঝিতে পারে, পণ্ডিতের লাগে ধন্ধ।
এই প্রবচনের উপর ভরসা রেখে এ হেঁয়ালির উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।
৬.
বলা বাহুল্য যে, কাব্য আর এনসাইক্লোপিডিয়া এক বৃন্তের দুটি ফুল নয়। কাব্য মানুষের অন্তর হতে আবির্ভূত হয়, আর এনসাইক্লোপিডিয়া বাহির থেকে সংগৃহীত। সুতরাং এ উভয়েই যে এক স্থানে ও এক ক্ষণে জন্মলাভ করেছে, এ কথা অবিশ্বাস্য। সুতরাং আমাদের ধরে নিতেই হবে যে, এ দুই পৃথক্ বস্তু; গোঁড়ায় পৃথক্ ছিল, পরে কালবশে জড়িয়ে গিয়েছে। তার পর প্রশ্ন ওঠে এই যে, কাব্যের স্কন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া ভর করেছে, না, এনসাইক্লোপিডিয়ার অন্তরে কাব্য কোনো ফাকে ঢুকে গেছে। এখন এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশ্ব অবশ্য কাব্যের পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু বিশ্বকোষ কাব্যের অনেক পরে নির্মিত হয়েছে। এ গ্রন্থের কথার বয়স ওর বক্তৃতার বয়সের চাইতে ঢের বেশি; অর্থাৎ ও-গ্রন্থের সার ওর ভারের চাইতে অনেক প্রাচীন। আর ভাগ্যিস ও-সারটুকু তার উপর চাপানো ভারের ভরে মারা যায় নি, তাই ও-কাব্য আজও বজায় আছে। ও-গ্রন্থের কাব্যাংশ অর্থাৎ সারাংশ যদি বিশ্বকোষের চাপে পিষে যেত, তাহলে মহাভারত হত অর্ধেক বৃহৎসংহিতা আর অর্ধেক বৃহৎকথা; অর্থাৎ তা সকলের পাঠ্য হত না, পাঠ্য হত এক দিকে বৃদ্ধের, অপর দিকে বালকের। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পণ্ডিতমণ্ডলী প্রায় একমত। তারা নানা শাস্ত্র ঘেঁটে এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, মূলে এ কাব্যের নাম ছিল ভারত, তার পরে তার নাম হয়েছে মহাভারত। এ সত্য উদ্ধারের জন্য, আমার বিশ্বাস, নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন ছিল না। বর্তমান মহাভারতেই ও-দুটি নামই পাওয়া যায়। আর ভারত যে মহাভারত হয়ে উঠেছে তার মহত্ত্ব ও গুরুত্বের গুণে, অর্থাৎ তার পরিমাণ ও ওজনের জন্যে, এ কথা আদিপূর্বেই লেখা আছে।
অতঃপর দেখা গেল যে, মহাভারতের পূর্বে ভারত নামক একখানি কাব্য ছিল। মহাভারত আছে, কিন্তু ভারত নেই। অতএব এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত গেল কোথায়? সে গ্রন্থ লুপ্ত হয়েছে, না, গুপ্ত হয়েছে? এ প্রশ্নের একটা সোজা উত্তর পেলেই আমরা বর্তমান মহাভারতের কোন্ অংশ তার অপরিমিত মহত্ত্ব ও গুরুত্বের কারণ, তা অনুমান করতে পারব। মহাত্মা তিলক এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তার বক্তব্য এই যে–
সরল শব্দার্থে ‘মহাভারত’ অর্থে ‘বড় ভারত’ হয়। বর্তমান মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উপাখ্যানসমূহের অতিরিক্ত মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা চব্বিশ হাজার, এবং পরে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমে উহার নাম ‘জয়’ ছিল। ‘জয়’ শব্দে ভারতীয় যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় বিবক্ষিত বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহাই প্রতীত হয় যে, ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা প্রথমে ‘জয়’ নামক গ্রন্থে করা হইয়াছিল, পরে সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যেই অনেক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়া উহাই ইতিহাস ও ধর্মাধর্মবিচারের ও নির্ণয়কারী এই এক বড় মহাভারতে পরিণত হইয়াছে।
অর্থাৎ জয় ওরফে ভারত-কাব্য লুপ্ত হয় নি, মহাভারতের অন্তরেই তা গা-ঢাকা নিয়ে রয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে মহাভারতের মহত্ত্ব ও গুরুত্বের চাপের ভিতর থেকে জয়ের ক্ষুদ্র দেহ উদ্ধার করা অসম্ভব। ভারত যে নুপ্ত হয় নি, এ বিষয়ে আমি মহাত্মা তিলকের মত শিরোধার্য করি, কারণ সে কাব্যের লুপ্ত হবার কোনো কারণ নেই। সেকালে ছাপাখানা ছিল না, সব গ্রন্থই হাতে লিখতে হত, সুতরাং উপযুক্ত লেখকের অভাবে বড় ভারতেরই লুপ্ত হবার কথা, ছোট ভারতের নয়। সেকালে একটানা শত-সহস্র শ্লোক লেখবার লোক যে কতদূর দুষ্প্রাপ্য ছিল তার প্রমাণ, স্বয়ং ব্রহ্মাও বেদব্যাসের মনঃকল্পিত গ্রন্থ লেখবার ভার গণেশের উপর দিয়েছিলেন। দেশে লেখবার মানুষ পাওয়া গেলে আর হিমালয় থেকে লম্বোদর দেবতাকে টেনে আনতে হত। ভগবান গজাননও যে ইচ্ছাসুখে এই বিরাট গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করতে রাজি হন নি, তার প্রমাণ তিনি লেখা ছেড়ে পালাবার এক ফন্দি বার করেছিলেন। তিনি ব্যাসদেবকে বলেন যে, আমি বৃথা সময় নষ্ট করতে পারব না। আপনি যদি গড়গড় করে শ্লোক আবৃত্তি করে যান, তাহলে আমি ফসফস্ করে লিখে যাব। আর আপনি যদি একবার মুখ বন্ধ করেন তো আমি একেবারে কলম বন্ধ করব। বেদব্যাস কি চালাকি করে হাঁপ ছেড়ে জিরিয়েছিলেন, অথচ হেরম্বকে দিয়ে আগাগোড়া মহাভারত লিখিয়ে নিয়েছিলেন, সে কথা তো সবাই জানে। গণেশকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেবার জন্য তিনি অষ্টসহস্র অষ্টশত শ্লোক রচনা করেন, যার অর্থ তিনি বুঝতেন আর শুকদের বুঝতেন, আর সঞ্জয় হয়তো বুঝতেন, হয়তো বুঝতেন না; সেই ৮৮০০ শ্লোক যদি কেউ মহাভারত থেকে বেছে ফেলতে পারেন, তাহলে তিনি আমাদের মহা উপকার করবেন। তবে জর্মান পণ্ডিত ছাড়া এ কাঁটা বাছবার কাজে আর কেউ হাত দেবেন না।
তার পর, বড় বই লেখাও যেমন শক্ত, পড়াও তেমনি শক্ত। এমন কি, সেকালের পণ্ডিত লোকেও বড় বই ভালোবাসতেন না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জর্মান পণ্ডিতদের মত হাজার হাজার পাতা বই গেলা এতদ্দেশীয়দের পক্ষে অসম্ভব। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদেব বিরাট গ্রন্থ যে ইষ্ট ছিল না, সে কথা মহাভারতেই আছে–
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্।
সুতরাং লেখার হিসেব থেকে হোক আর পড়ার হিসেব থেকেই হোক, দু হিসেব থেকেই আমরা মানতে বাধ্য যে, ভারত লুপ্ত হয় নি, ও-কাব্য মহাভারতের অন্তরে সেই ভাবে অবস্থিতি করছে, যে ভাবে শকুন্তলার আংটি মাছের পেটে অবস্থিতি করেছিল।
আমরা যদি মহাভারতের ভিতর থেকে ভারতকে টেনে বার করতে পারি, তাহলে ভারতের অন্তরে ও অঙ্গে কোন্ কোন্ উপাখ্যান ইতিহাস দর্শন ও ধর্মাধর্মের বিচার প্রক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার একটা মোটামুটি হিসেব পাই। আর যদি ধরে নিই যে, মহাভারতের অতিরিক্ত মালমসলা সব ঐ ভারত-কাব্যের ভিতর interpolated হয়েছে, তাহলে অবশ্য ঐ শ্লোক্যুপের ভিতরে ভারতের সন্ধান আমরা পাব না। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি গ্রীক দেবতা হারকিউলিসের মত ওরকম পঙ্কোদ্ধার করতে প্রবৃত্ত হবেন। অপর পক্ষে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের মত এই জটিল গ্রন্থের Gordian knot যদি আমরা দ্বিখণ্ড করতে পারি, তাহলে হয়তো মহাভারত থেকে ভারতকে পৃথক্ করে নিতে পারি।
৭.
ইন্টারপোলেশনের দৌলতেই ভারত যে মহাভারতে পরিণত হয়েছে, সে বিষয়ে দেশি বিলেতি সকল আধুনিক পণ্ডিত একমত।
কিন্তু এই ইন্টারপোলেশন, ভাষান্তরে ‘প্রক্ষিপ্ত’ কথাটা, তারা যে কি অর্থে ব্যবহার করেন, সেটা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।
যদি তাদের মত এই হয় যে, যেমন মোরগের পেটে চাল পুরে দিয়ে একাধারে কাবাবু ও পোলাও বানানো হয়, তেমনি ভারতের অন্তরে নানা বস্তু নানা যুগে পুরে দিয়ে তার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সাধন করা হয়েছে, তাহলে সে মত আমি সন্তুষ্ট মনে গ্রাহ্য করতে পারি নে।
আমার বিশ্বাস, বর্তমান মহাভারতের কতক অংশ ভারতের ভিতর পুরে দেওয়া হয়েছে, এবং অনেক অংশ তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রক্ষিপ্ত অংশের বিচার এখন স্থগিত রেখে যদি আমরা সংযোজিত অংশকে ভারতকাব্য থেকে বিযুক্ত করতে পারি, তাহলে আমাদের সমস্যা অনেক সরল হয়ে আসে।
আমরা যদি সাহস করে এক কোপে মহাভারতকে দ্বিখণ্ড করে ফেলতে পারি, তাহলে, আমার বিশ্বাস, ভারতকে মহাভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি। বর্তমান মহাভারতের নয় পর্ব হচ্ছে প্রাচীন ভারত, আর তার বাদবাকি নয় পর্ব হচ্ছে অর্বাচীন মহাভারত–এই হিসেবটাই হচ্ছে গণিতের হিসেবে সোজা; অতএব অপণ্ডিতদের কাছে গ্রাহ হওয়া উচিত।
প্রথম নয় পূর্বের ভিতর অবশ্য অনেক প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে, যা পূর্বে ভারতকাব্যের অঙ্গস্বরূপ ছিল না; কিন্তু শেষ নয় পূর্বের ভিতর সম্ভবত এমন একটি কথাও নেই, যা পূর্বে ভারতকাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
সংক্ষেপে দুইখানি বই একসঙ্গে জুড়ে মহাভারত তৈরি করা হয়েছে। এ দুইখানি গ্রন্থকে পূর্বভারত ও উত্তরভারত আখ্যা দেওয়া চলে। সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে এ রকম কাব্য আরও অনেক আছে। কাদম্বরী কুমারসম্ভব মেঘদূত প্রভৃতির এইরকম দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ অবশ্য একই হাতের লেখা এবং একই কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গ। কাদম্বরীর পূর্বভাগ বাণভট্টের রচনা, আর উত্তরভাগ তাঁর পুত্রের। কুমারসম্ভবের পূর্বভাগ কালিদাসের রচনা, আর উত্তরভাগ, আর যারই লেখা হোক, কালিদাসের লেখা নয়। এমন কি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড যে বাল্মীকির লেখনী প্রসূত নয় সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।
৮
মহাভারতকে এ রকম দ্বিধাবিভক্ত করা নেহাত গোয়ারতুমি নয়। সত্যসত্যই দুটি অধখানিকে গ্রথিত করে মহাভারত নামে একখানি গ্রন্থ করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ চিরকালই রয়ে যাবে, কেননা মহাভারত সংক্রান্ত বড় বড় আবিষ্কার সম্বন্ধে সমান সন্দেহ রয়ে গেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ডালমান Daliluann নামক জনৈক ধনুর্ধর জর্মান পণ্ডিত অজীবন গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহাভারত খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। অপর পক্ষে? হোলৎসমান Holtzmann নামক অপর-একটি সমান ধনুর্ধর জর্মান পণ্ডিত অজীবন গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহাভারত খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই উভয় আবিষ্কারই যুগপৎ সমান সত্য হতে পারে না। ফলে এর একটি ও সত্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ লোকের মনে থেকেই যায়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জর্মান পণ্ডিতদের প্রতি ভক্তি কারও কমে নি। বিদ্বান্ ব্যক্তিদের পদানুসরণ করেই আমি আমার মত ব্যক্ত করছি। সে মত যার খুশি গ্রাহ করতে পারেন, যার খুশি অগ্রাহ্য করতে পারেন; শুধু আমার মতকে সম্পূর্ণ গাঁজাখুরি মনে করবেন না। আমার মত আমি শূন্যে খাড়া করি নি। এ সত্যের মূল মহাভারতের ভিতরেই আছে। আপনাদের পূর্বে বলেছি যে, পুরাকালে ভারত-কাব্যের অপর নাম ছিল জয়-কাব্য; অর্থাৎ এ কাব্যে ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের কথা; সুতরাং যুদ্ধজয়ের পরবর্তী কোনো বিষয়ের বর্ণনা বা আলোচনা এতে ছিল না। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন যে, মহাভারত হচ্ছে যুদ্ধ প্রধান গ্রন্থ, এবং ও-কাব্যের প্রধান বিষয় যা, তা শেষ। হয়েছে সৌপ্তিকপূর্বে। এ কথা যে সত্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। যুদ্ধ করবার লোক না থাকলে আর যুদ্ধ করা যায় না। আর সৌপ্তিকপূর্বের শেষে দেখতে পাই যে, অশ্বথামা মুমূষু দুর্যোধনকে বলেছেন যে, উভয় পক্ষের সকল যোদ্ধা নিহত হয়েছে। অবশিষ্ট আছে শুধু কৌরব পক্ষের তিনজন কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও স্বয়ং অশ্বত্থামা। অপরপক্ষে পাণ্ডবদের ভিতর অবশিষ্ট আছে সাতজন, পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কৃষ্ণ। এ কথা বলেই অশ্বত্থামা চলে গেলেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আশ্রমে, কৃতবর্মা স্বরাষ্ট্রে ও কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে। এইখানেই ভারত-নাটকের যবনিকা পতন হয়েছে। এর পর মহাভারতে যা আছে সে হচ্ছে যুদ্ধের নয়, শান্তির কথা। বর্তমান মহাভারত অবশ্য এদেশের ওঅর অ্যাণ্ড পীস নামক মহাকাব্য। কিন্তু মূল ভারত ছিল ইলিঅডের মত শুধু যুদ্ধকাব্য। কাব্যকে আমরা ফুল বলি। এ হিসেবে সৌপ্তিকপর্বকেই আমরা ভারতকাব্যের শেষ পর্ব বলে স্বীকার করতে বাধ্য। আদিপূর্বে আছে যে, মহাভারত নামক মহাবৃক্ষের সৌপ্তিকপর্ব হচ্ছে প্রসূন, আর শান্তিপর্ব মহাফল। ফুল যখন ফলে পরিণত হয়, তখনই তা কাব্যের বহিভূত হয়ে পড়ে। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে এই উত্তরভারতে কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত আর কোন্ শ্লোক নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, কারণ ও-গ্রন্থ আগাগোড়াই প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত অংশের সন্ধান করতে হবে পূর্বভারতে। এতে এই খোঁজাখুজির কাজটা অর্ধেক কম হয়ে আসে কি না?
৯.
সৌপ্তিকপর্ব ভারত-কাব্যের অন্তভূতি স্বীকার করলে আমার কল্পিত বিভাগ দুটি ঠিক সমান হয় না। কারণ সৌপ্তিকপর্ব হচ্ছে বর্তমান মহাভারতের দশম পর্ব। কিন্তু আসলে আমার হিসেবে ভুল হয় নি। মহাভারতের একটি পর্ব যা পূর্বভাগে স্থান পেয়েছে, তা আসলে উত্তরভাগের জিনিস। আদিপর্ব হচ্ছে মহাভারতের অন্তপর্ব। ও-পূর্বের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে আমরা যাকে বলি Preface, দ্বিতীয় অধ্যায় Table of contents এবং তার পরবর্তী কথাপ্রবেশপর্ব হচ্ছে Introduction। এখন এ কথা কে না জানে যে, মুখপত্র, সূচি ও ভূমিকা বইয়ের গোঁড়াতে ছাপা হলেও লেখা হয় সবশেষে। আমার মত যে সত্য, তার প্রমাণ ‘আদি’ শব্দের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ স্পষ্ট বলেছেন–
আদিত্বঞ্চাস্ত ন প্রাথম্যাৎ।
তিনি অবশ্য এর পরে একটা কথা জুড়ে দিয়েছেন, যথা–
কিন্তু সর্বেষামাদিরুৎপত্তিরিহ কীর্ত্যতে ইতি।
কোনো কাব্যের গোঁড়াতেই কবি কখনো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কীর্তন করেন না। এই বিশ্বসৃষ্টির বিবরণ ভারত-কাব্যের বিষয় নয়, ভারতবিশ্বকোষের অঙ্গ।
মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করবার আরএকটি মুশকিল আছে। ভারত-কাব্য সৌপ্তিকপূর্বে শেষ করলে ও-কাব্যের ভিতর থেকে স্ত্রীপর্ব বাদ পড়ে। কিন্তু ও-পর্বকে ভারতের কাব্যাংশ থেকে আমি কিছুতেই বহিষ্কৃত করতে পারি নে। গান্ধারীর বিলাপ না থাকলে ভারত-কাব্যের অঙ্গহানি হয়। অপরপক্ষে ও-বিলাপকে আমি কিছুতেই উত্তর ভারতের অন্তভূত করতে পারি নে। এপিকের সুর যার কানে লেগেছে সে ব্যক্তি কখনোই স্ত্রীপর্বকে এনসাইক্লোপিডিয়ার অঙ্গ বলে স্বীকার করতে পারে না। এর প্রমাণস্বরূপ আমি গান্ধারীর মুখের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। শ্মশানে পরিণত যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃখের চরম দশায় উপনীত গান্ধারী যখন শ্রীকৃষ্ণকে বিগতেশ্বর কুরুকুলাঙ্গনাদের একে একে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজের কন্যা দুঃশলাকে দেখিয়ে বলেন–
হা হা ধিগ্দুঃশলাং পশ্য বীতশোকভয়ামিব।
শিরোভরনাসাঙ্গ ধাবমানামিতস্ততঃ।।
যাঁরা শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব লিখেছেন, তাঁরা শতসহস্র শ্লোক লিখলেও এর তুল্য একটি শ্লোক লিখতে পারেন না। এর প্রতি কথার ভিতর থেকে মহাকবির হাত ফুটে বেরচ্ছে। ভারত-কাব্যের ভিতর যদি স্ত্রীপর্বকে স্থান দেওয়া যায়, তাহলে সেখান থেকে আর-একটি পর্বকে স্থানচ্যুত করতে হয়। আমি বনপর্বকে পূর্বভারত থেকে বহিষ্কৃত করতে প্রস্তুত আছি। ও পূর্বের যে পনেরো আনা তিন পাই প্রক্ষিপ্ত, এ বিষয়ে সকল পণ্ডিত, মায় তিলক, একমত। সেই এক পাই আমি বিরাটপূর্বের অন্তভূত করে, বাদবাকি অংশটি উপাখ্যানপর্ব নামে উত্তরভারতে স্থান দিতে চাই। আর তাতে যদি কারও আপত্তি থাকে তাহলে বলি, পূর্বভারত দশ পর্ব, আর উত্তরভারত অষ্ট পর্ব।
১০
আমি জনৈক বন্ধুর মুখে শুনলুম যে, শান্তিপর্ব থেকে শুরু করে স্বর্গারোহণপর্ব পর্যন্ত অষ্টপর্ব যে মহাভারতের অন্তরে পাইকেরি হিসেবে প্রক্ষিপ্ত, এ কথা নাকি সবাই জানে। যদি তাই হয় তা আমার এ গবেষণার ফল হচ্ছে পণ্ডিতের তেলা মাথায় তেল ঢালা। কিন্তু আমার এই গবেষণা যে বৃথা হয় নি, তার প্রমাণ, মহাত্মা তিলক এ সত্য হয় জানতেন না, নয় মানতেন না। আর পাণ্ডিত্যের হিসেবে তিনি কোনো জর্মান পণ্ডিতের চাইতে কম ছিলেন না। তিনি বলেছেন যে, বর্তমান মহাভারত এক হাতের লেখা। বর্তমান মহাভারত যে এক হাতের লেখা নয়, এবং এক সময়ের লেখা নয়, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমি এই অনধিকারচর্চা করতে বাধ্য হয়েছি।
আমার আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, গীতা মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত কি না। বর্তমান মহাভারতের শেষ আট পর্ব হেঁটে দিলেও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, কেননা গীতা পূর্বভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তভূত, উত্তরভারতের নয়। সুতরাং যে সমস্যার মীমাংসা করতে হবে সে হচ্ছে এই যে, গীতা ভারত-কাব্যের অঙ্গ, না তার অঙ্গস্থ পরগাছা? গীতাকাব্যের রূপ দেখেই আমরা ধরে নিতে পারি নে যে, ও ফুল ভারত কাব্যের অন্তর থেকে ফুটে উঠেছে। অর্কিডের ফুলও চমৎকার, কিন্তু তার মূল ঝোলে আকাশে।
উক্ত বিচার আমার সময়ান্তরে করবার ইচ্ছা আছে। এস্থলে শুধু একটা কথা বলে রাখি। আদিপর্বে ভীষ্মপর্বকে বিচিত্রপর্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পূর্বের এই বৈচিত্র্যের কারণ, এতে যুদ্ধ প্রসঙ্গ ব্যতীত হরেকরকমের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ আছে। ভীষ্মপর্ব এক হাতের লেখা নয়। এসব প্রসঙ্গের বেশির ভাগই প্রক্ষিপ্ত এবং গীতাও তাই কি না, সেইটিই বিচার্য।
১৩৩৪ কার্তিক
————–
(১) শ্ৰীমদ্ভগবদগীতারহস্য। অথবা কৰ্ম্মযোগশাস্ত্র। কলিকাতা, ১৯২৪ খ্রী
(২) মহাভারতের উপরোক্ত শ্লোকের আমি কেবল একটি শব্দ বদলে দিয়েছি, ‘দুঃখস্যাস্য’ পরিবর্তে গ্রন্থস্যাস্য বসিয়ে দিয়েছি। আশা করি, তাতে অর্থের কোনো ক্ষতি হয় নি।
রামমোহন রায়
কোনো-একটি সাহিত্যসভায় পড়া হবে বলে লিখিত
আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে আপনাদের সুমুখে উপস্থিত হয়ে দু-চার কথা বলবার জন্যে বহুদিন ধরে অনুরোধ করে আসছেন। কতকটা অবসরের অভাবের দরুন, কতকটা আলস্যবশতঃ সে অনুরোধ আমি এতদিন রক্ষা করতে পারি নি। তিনি যে বিষয়ে আমাকে বলতে অনুরোধ করেন, সে বিষয়ে ভালো করে কিছু বলবার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হওয়া দরকার, এবং তার জন্য কতকটা অবসরও চাই, কতকটা পরিশ্রমও চাই। রামমোহন রায় সম্বন্ধে যেমন-তেমন করে যাহোক একটা প্রবন্ধ গড়ে তুলতে আমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হয়। যে ব্যক্তিকে আমি এ যুগের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলে মনে করি, তাকে মৎফরাক্কা রকম একটা সার্টিফিকেট দিতে উদ্যত হওয়াটা আমার মতে ধৃষ্টতার চরম সীমা।
শেষটা আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় যখন আমাকে কথোপকথনচ্ছলে এই মহাপুরুষের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার অনুমতি দিলেন, তখন আমি তার উপরোধ এড়িয়ে যাবার কোনো পথ দেখতে পেলুম না।।
কিছুদিন পূর্বে প্রবাসী পত্রিকা এ যুগের বাংলাদেশের সবচাইতে বড় লোক কে, পাঠকদের কাছ থেকে এই প্রশ্নের জবাবু চেয়েছিল। পাঠকদের ভোটে স্থির হয়ে গেল যে, সে ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়। দেশের লোক যে এ সত্য আবিষ্কার করেছে, এ দেখে আমি মহা খুশি হলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনে একটি প্রশ্নও জেগে উঠল। রামমোহন রায় যে বাংলার, শুধু বাংলার নয়, বর্তমান ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ, এ সত্য বাঙালি কি উপায়ে আবিষ্কার করলে? রামমোহন রায়ের লেখার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে এমন লোক আমার পরিচিতের মধ্যে একান্ত বিরল, অথচ এদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন যথোচিত সুশিক্ষিত এবং দস্তুরমত স্বদেশভক্ত। লোকসমাজে অনেকেরই বিশ্বাস যে, রামমোহন রায় বাংলা গদ্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনি বাংলার সর্বপ্রথম গদ্যলেখক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কিন্তু যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তা এই যে, তিনি হচ্ছেন বাংলা গদ্যের প্রথম লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রধান লেখক। অথচ তার লেখার সঙ্গে বাংলা লেখকদেরও পরিচয় এত কম যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথা লিখতেও কুণ্ঠিত হন না যে, রামমোহন রায় ইংরেজি গদ্যের অনুকরণে বাংলা গদ্য রচনা করেছিলেন। এর পর যদি কেউ বলেন যে, শংকরের গদ্য হার্বার্ট স্পেন্সারের অনুকরণে রচিত হয়েছিল তাতে আশ্চর্য হবার কোনোই কারণ নেই।
২.
এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, রামমোহন রায় এই অল্পকালের মধ্যেই ইতিহাসের বহির্ভূত হয়ে কিংবদন্তির অন্তর্ভূত হয়ে পড়লেন কেন। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, সাধারণতঃ লোকের মনে এই রকম একটা ধারণা আছে যে, রামমোহন রায় বাঙালি জাতির একজন মহাপুরুষ নন, কিন্তু বাংলার একটি নব ধর্মসম্প্রদায়ের একজন মহাজন।
এ ভুল ধারণার জন্য দোষী কে? ব্রাহ্মসমাজ না হিন্দুসমাজ? এ প্রশ্নের উত্তর আজকের সভায় দিতে আমি প্রস্তুত নই, কেননা তা হলেই নানারূপ মতভেদের পরিচয় পাওয়া যাবে, নানারূপ তর্ক উঠবে এবং সে তর্ক শেষটা বাকবিতণ্ডায় পরিণত হবে। ইংরেজদের ভদ্রসমাজে ধর্ম ও পলিটিক্সের আলোচনা নিষিদ্ধ, কেননা বহুকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে প্রমাণ হয়েছে যে, এই দুই বিষয়ের আলোচনায় লোকে সচরাচর ধৈর্যের চাইতে বীর্য বেশির ভাগ প্রকাশ করে। ফলে বন্ধুবিচ্ছেদ জ্ঞাতিবিরোেধ প্রভৃতি জন্মলাভ করে, এক কথায় হাত হাত সমাজের শান্তিভঙ্গ হয়। এ ক্ষেত্রে আমি রামমোহন রায়ের ধর্মমতের আলোচনায় যদি প্রবৃত্ত হই, তাহলে তার সমসাময়িক সেই পুরোনো কলহের আবার সৃষ্টি করব। এক শ বৎসর আগে রামমোহন রায়কে তার বিপক্ষ দলের কাছ থেকে যেসকল যুক্তিতর্ক শুনতে হত, আজকের দিনে আমাদেরও সেইসব যুক্তিতর্ক শুনতে হবে। রামমোহন রায়ের রচিত পথ্যপ্রদান প্রভৃতি পড়ে দেখবেন, সে যুগের ধর্মসংস্থাপনকারীরা যে ভাবে যে ভাষায় তার মতের প্রতিবাদ করেছিলেন, এ যুগেও সেই ভাব সেই ভাষায় নিত্য প্রকাশ পায়। এই এক শ বৎসরের ভিতর মনোরাজ্যে আমরা বড় বেশিদূর এগোই নি। অএব এ ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের ধর্মমত সম্বন্ধে নীরব থেকে তার সামাজিক মতেরই যুৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। তার থেকেই দেখতে পাবেন যে, তার চাইতে বড় মন ও বড় প্রাণ নিয়ে এ যুগে ভারতবর্ষে অপর কোনো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নি। মানুষ মাত্রেরই জ্ঞানের আশ্রয় হচ্ছে দুটি বাইরের জিনিস; এক মানবসমাজ, আর-এক বিশ্ব। ইংরেজি দর্শনের ভাষায় যাকে cosmic consciousness এবং social consciousness বলে, মানুষমাত্রেরই মনে এ দুই consciousness অল্পবিস্তর আছে।
এ বিশ্বের অর্থ কি, এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, সে সম্বন্ধ ইহজীবনের। কি অনন্তকালের, এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে কসমিক কশাসনেস; এবং সকল ধর্ম, সকল দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এইসব প্রশ্নের জবাবু দেওয়া। অপর পক্ষে ইহজীবনে কি উপায়ে আমার অভ্যুদয় হবে, সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, তার প্রতি আমার কর্তব্যই বা কি, কিরূপ কর্ম সমাজের পক্ষে এবং সামাজিক ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলকর, এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে সোশ্যাল কশাসনেস; তাই পলিটিক্স আইন শিক্ষা প্রভৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের মঙ্গল সাধন করা।
নিত্য দেখতে পাই যে, এ দেশের লোকের মনে এদানিক এই ভুল বিশ্বাস জন্মলাভ করেছে যে, ভারতবর্ষে পুরাকালে ছিল একমাত্র কসমিক কশাসনেস এবং ইউরোপে বর্তমানে আছে শুধু সোশ্যাল কন্শানেস। আমাদের দেশের শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে এর প্রতিবাদ করছে। যাকে আমরা মোক্ষশাস্ত্র বলি, তা কমিক কশাসনেস হতে উদ্ভূত, আর যাকে আমরা ধর্মশাস্ত্র বলি, তা সোশ্যাল কশানেস হতে উদ্ভূত। জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ সেকালে ছিল ঠিক উলটো উলটো পথ। ব্ৰহ্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে কর্মজিজ্ঞাসার যে কি প্রভেদ, তা যিনি বেদান্তের দু পাতা উলটেছেন তিনিই জানেন। এ দুই যে। বিভিন্ন শুধু তাই নয়, এ উভয়ের ভিতর স্পষ্ট বিরোধ ছিল। কর্ম যখন ক্রিয়াকলাপে পরিণত হয় তখন জ্ঞানকাণ্ড তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য, আর ধর্ম যখন কর্মহীন জ্ঞানে পরিণত হয় তখন কর্মকাণ্ড তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়। জ্ঞানকর্মের সমন্বয় করবার জন্য ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের কাছে এ সত্য প্রত্যক্ষ ছিল যে, কর্মহীন জ্ঞান পঙ্গু এবং জ্ঞানহীন কর্ম অন্ধ। রামমোহন রায় এদেরই বংশধর, এদের পাঁচজনেরই একজন।
৩.
তিনি যে জ্ঞানকর্মের সমন্বয় করতে ব্ৰতী হয়েছিলেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই, সেকালে তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে, তিনি গৃহী হয়েও ব্ৰহ্মজ্ঞানী হবার ভান করতেন, এক কথায় তিনি ছিলেন একজন ‘ভাক্তজ্ঞানী’।
এই ‘ভাক্ত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গৌণ, অপ্রধান ইত্যাদি। এই বিশেষণে বিশেষিত হতে রামমোহন রায় কখনোই আপত্তি করেন নি। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে, তিনি যে ব্রহ্মের স্বরূপ জানেন, এমন স্পর্ধা তিনি কখনোই রাখেন নি। তবে গৃহীর পক্ষে যে বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপই একমাত্র সেব্য ধর্ম এবং গৃহস্থের পক্ষে যে ব্ৰহ্মনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব, এ কথা যেমন ন্যায়বিরুদ্ধ, তেমনি অশাস্ত্রীয়। এ কথার উত্তরে ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা যোগবশিষ্ঠের একটি বচন তার গায়ে ছুড়ে মেরেছিলেন। সে বচনটি হচ্ছে এই–
সংসারবিষয়াসক্ত ব্ৰহ্মজ্ঞোস্মীতিবাদিনম্।
কর্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা।।
অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংসার সুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্ৰহ্মজ্ঞানী ইহা কহে, সে কর্ম-ব্ৰহ্ম উভয় ভ্রষ্ট, অতএব অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাজ্য হয়।
এ সম্বন্ধে রামমোহন রায় বলেন—
যোগবাশিষ্ঠে ভাক্তজ্ঞানীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে।
এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই দেখিয়ে দেওয়া যে, কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের একসঙ্গে চর্চা করা যেতে পারে কি না, এইটিই ছিল সে যুগের আসল বিবাদস্থল। এ বিবাদ আমরা আজ করি নে, কেননা দেশ সুদ্ধ লোক এখন গী তাপন্থী; এবং আপনারা সকলেই জানেন যে, লোকের ধারণা যে, গীতায় শুধু জ্ঞানকর্মের নয়, সেই সঙ্গে ভক্তিরও সমন্বয় করা হয়েছে। দেশসুদ্ধ লোক আজ যে পথের পথিক হয়েছে, সে পথের প্রদর্শক হচ্ছেন রামমোহন রায়। সুতরাং ধর্মমত সম্বন্ধেও তিনিই হচ্ছেন এ যুগের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান মহাজন। যে শাস্ত্রের বচনসকল আজ শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল লোকের মুখে মুখে ফিরছে, রামমোহন রায়কে সেই বেদান্তশাস্ত্রের আবিষ্কর্তা বললেও অত্যুক্তি হয় না। আপনারা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, সেকালে একদল পণ্ডিত তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে, উপনিষদ বলে সংস্কৃত ভাষায় কোনো শাস্ত্রই নেই, ঈশ কেন কঠ প্রভৃতি নাকি তিনি রচনা করেছিলেন। এ অভিযোগ এত লোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন যে, রামমোহন এই মিথ্যা অভিযোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবার জন্য প্রকাশ্যে এই জবাবু দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই কলিকাতা শহরে শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের বাড়িতে গেলেই সকলে দেখতে পাবেন যে, বেদান্তশাস্ত্রের সকল পুঁথিই তার ঘরে মজুত আছে। বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের নাম উল্লেখ করবার কারণ এই যে, তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের বিপক্ষদলের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত।
স্কচ দার্শনিক ড্যুগাল্ড স্টুয়ার্ট Dugald Stewart বলেছিলেন যে, সংস্কৃত বলে কোনো ভাষাই নেই, ইংরেজদের ঠকাবার জন্য ব্রাহ্মণেরা ঐ একটি জাল ভাষা বার করেছে। এ কথা শুনে এককালে আমরা সবাই হাসতুম, কেননা সেকালে আমরা জানতুম না যে, এই বাংলাদেশেই এমন একদল টোলের পণ্ডিত ছিলেন, যাদের মতে বেদান্ত বলে কোনো শাস্ত্রই নেই, বাঙালিদের ঠকাবার জন্য রামমোহন রায় ঐ একটি জাল শাস্ত্র তৈরি করেছেন। এই জালের অপবাদ থেকে রামমোহন রায় আজও মুক্তি পান নি। আমাদের শিক্ষিতসমাজে আজও এমন-সব লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের বিশ্বাস মহানির্বাণতন্ত্র রামমোহন রায় এবং তার গুরু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী এই উভয়ে মিলে জাল করেছেন। এরা ভুলে যান যে, দলিল লোকে জাল করে শুধু আদালতে পেশ করবার জন্য। এই কারণেই টোলের পণ্ডিতমহাশয়ের দত্তকচন্দ্রিকা নামক একখানি গোটা স্মৃতিগ্ৰন্থ রাতারাতি জাল করে ইংরেজের আদালতে পেশ করেছিলেন। সে জাল তখন ধরা পড়ে নি, পড়েছে এদানিক। ঈশ কেন কঠ, এমনকি মহানির্বাণতন্ত্র পর্যন্ত, কোনো আদালতে গ্রাহ্য হবে না, ওসবই irrelevant বলে rejected হবে। সুতরাং রামমোহম রায়ের পক্ষে মোক্ষশাস্ত্র জাল করবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। তবে যে লোকে মহানির্বাণকে জাল মনে করে, তার কারণ তারা বোধ হয় দত্তকচন্দ্রিকাকেও genuine মনে করে। এই শ্রেণীর বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মূলে আছে। একমাত্র জনশ্রুতি। এই এক শ বৎসরের শিক্ষাদীক্ষার বলে আমাদের বিচারবুদ্ধি যে আজও ফণা ধরে ওঠে নি, তার কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সে বুদ্ধি স্বল্পজ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর আটকে পড়েছিল, আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সে বুদ্ধি আমাদের অতিজ্ঞানের চাপে মাথা তুলতে পারছে না। আমি আশা করি, একবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙালির বিদ্যার বোঝা কতকটা লঘু হয়ে আসবে, আর তখন বাঙালির বুদ্ধি স্বচ্ছন্দে খেলে বেড়াবার একটু অবসর পাবে।
৪.
রামমোহন রায় সম্বন্ধে আর-একটি লৌকিক ভুল ধারণা এই যে, তিনি ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার একটি product, অর্থাৎ ইউরোপের কাব্য ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের প্রভাবেই তাঁর মন তৈরি হয়েছিল, এক কথায় তিনি আমাদেরই জাত। আমার ধারণা যে অন্যরূপ সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। আমি আজ বছর তিনেক আগে এই মত প্রকাশ করি যে–
Rengal produced in the last century a inan of colossal intellect and is marvellous clairvoyance — Rajah Ram Mohan Roy….British India up to now has not procluced a greater mind, and he remains for all time the supreme representative of the spirit of the new age and the genuancentd əkda kuranation from the pinnacle of Indian culture and saw and welcomed all that was living and life-giving in it.
আমি অতঃপর আপনাদের কাছে যা কিছু নিবেদন করব, তা সবই স্বমত সমর্থন করবার অভিপ্রায়ে।
রামমোহন রায় যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করবার পূর্বে একমাত্র ন্যায় এবং যুক্তির সাহায্যে ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার দলিল আছে। এ বিষয়ে তিনি কতক আরবি এবং কতক ফারসি ভাষায় যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আজকালকার ভাষায় যাকে স্বাধীন চিন্তা বলে তা তিনি কোনো বিলেতি গুরুর কাছে শিক্ষা করেন নি। নির্ভীকতায় চিন্তাশীলতায় তার হাতের এই প্রথম রচনা Millএর Three Essays on Religion প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে এক আসন গ্রহণ করবার উপযুক্ত।
তার পর তার বাংলা ও ইংরেজি লেখার সঙ্গে যার পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, পৌত্তলিকতার মত খৃস্টানধর্মকেও তিনি সমান প্রত্যাখ্যান করেন। তার মতে ও-ধর্মও আসলে একটি পৌরাণিক ধর্ম, অতএব তার মত শংকরের শিষ্যের নিকট তা অগ্রাহ। রামমোহন রায়কে শংকরের শিষ্য বলায় আমি নিজের মত প্রকাশ করছি নে। গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮) পড়ে দেখবেন যে, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, তিনি আচার্যের শিষ্য। আজকের দিনে এ শিষ্যত্ব অস্বীকার করতেই আমরা সাহসের পরিচয় দিই; কিন্তু সেকালে এ কথা স্বীকার করায় তিনি অতিসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে তখন বৈষ্ণবধর্মের প্রতিপত্তি সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে অপ্রতিহত ছিল। আর যারা চৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করেছেন তারাই জানেন যে, উক্ত ধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন যে, তিনি বেদান্ত মানেন কিন্তু আচার্য মানেন না, অর্থাৎ তিনি উপনিষদ্ মানেন কিন্তু তার শাংকরভাষ্য মানেন না। সে যাই হোক, এ কথা নিঃসন্দেহ যে, ইউরোপের ধর্মমত রামমোহন রায়ের মনের উপর প্রভুত্ব করে নি।
তার পর ইউরোপের প্রাচীন কিংবা অর্বাচীন দর্শনের সঙ্গে যে তার কোনোরূপ পরিচয় ছিল তার প্রমাণ তার লেখা থেকে পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, সে শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও তার শিক্ষা তার মনের উপর দিয়ে অয়েলক্লথের উপর দিয়ে জল যে রকম গড়িয়ে যায়, সেই ভাবে গড়িয়ে গিয়েছিল, তাতে করে তার মনকে ভেজাতে পারে নি।
অতএব আমি জোর করে বলতে পারি যে, রামমোহনের cosmic consciousness ছিল ষোলো আনা ভারতবর্ষীয়। সত্য কথা বলতে গেলে তিনি এ যুগে বাংলাদেশে প্রাচীন আর্য মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে মনের পরিচয় আমি এখানে দু কথায় দিতে চাই। আপনারা সকলেই জানেন যে কান্টের দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত : প্রথম pure reason, দ্বিতীয় practical reason, আর তৃতীয় esthetic judgment। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষীয় আর্যেরা যার বিশেষভাবে চর্চা করেছিলেন, সে হচ্ছে এক pure reason, আরএক practical reason; এবং রামমোহনের অন্তরে এই দুই reasonই পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। তিনি অলংকারশাস্ত্রকে কখনো দর্শনশাস্ত্র বলে গ্রাহ্য করেন নি, রসতত্ত্বকে আত্মতত্ত্ব বলে ভুল করেন নি, অর্থাৎ মানুষের মনের esthetic অংশের তার কাছে বিশেষ কিছু মর্যাদা ছিল না। বেদান্তের ধর্ম spiritual, কিন্তু emotional নয়; মীমাংসার ধর্ম ethical, কিন্তু emotional নয়। অপর পক্ষে খৃস্টান বৈষ্ণব মুসলমান প্রভৃতির ধর্মে emotional অংশ অতি প্রবল এবং সকল দেশের সকল মূর্তিপূজার মূলে মানুষের সৌন্দর্যবোধ আছে।
পাছে আমার কথা কেউ ভুল বোঝেন সেইজন্য এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, emotion শব্দ আমি মানুষের প্রতি মানুষের রাগদ্বেষ অর্থে ই ব্যবহার করেছি, কেননা anthropomorphic ধর্মমাত্রেরই সেই emotion হচ্ছে যুগপৎ ভিত্তি ও চুড়া। এ ছাড়া অবশ্য cosmic emotion বলেও একটি মনোভাব আছে, কেননা তা না থাকলে মানুষের মনে cosmic consciousness জন্মাতই না। আদিরসই এ জগতে একমাত্র রস নয়, অনাদিরস বলেও একটি রস আছে; যারা এ রসের রসিক তাঁদের কাছেই উপনিষদ্ হচ্ছে মানবমনের গগনচুম্বী কীর্তি। বলা বাহুল্য, মানুষ মাত্রেরই মনে এই উভয়বিধ emotionএর স্থান আছে। এর মধ্যে কার মনে কোটি প্রধান সেই অনুসারেই তার ধর্মমত আকার ধারণ করে।
কিছুদিন পূর্বে রামমোহন রায়ের একটি নাতিদীর্ঘ জীবনচরিত ইংরেজি ভাষায় বিলাতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার তার নাম গোপন রেখেছেন। এ পুস্তকে তার সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। তার মধ্যে একটি কথা হচ্ছে এই যে, তিনি বিলাতে গিয়ে খৃস্টধর্মের প্রতি অনুকূল হয়েছিলেন, এবং, লেখকের বিশ্বাস, তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে সম্ভবতঃ খৃস্টধর্ম অবলম্বন করতেন। এ কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে তিনি যে উক্ত ধর্মের সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ের ফলে তার প্রতি অনুকূল হয়েছিলেন, এ কথা গ্রাহ্য করায় বাধা নেই। বাইবেলের যে অংশ, রামমোহনের ভাষায় বলতে হলে, বড়াই বুড়ির কথায় পরিপূর্ণ, তিনি সেই অংশের উপরেই বরাবর তার বিপবাণ বর্ষণ করে এসেছিলেন; কিন্তু খৃস্টধর্মের যে অংশ spiritual এবং ethical সে অংশের প্রতি অনুকূল হওয়া ছাড়া উদারচেতা লোকের উপায়ান্তর নেই। আর রামমোহনের স্বভাবের আর যে দোষই থাকুক তিনি সংকীর্ণমনা ছিলেন না। ধর্ম সম্বন্ধে তার অন্তরে যে গোঁড়ামির লেশমাত্র ছিল না, তিনি যে একটি নতুন সম্প্রদায় গড়তে চান নি, কিন্তু স্বজাতিকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, তার পরিচয় আদিব্রাহ্মসমাজের ট্রস্ট ভীডে পাবেন। পৃথিবীতে আমরা দু জাতীয় অতিমানুষের সাক্ষাৎ পাই, এক যারা saviour অর্থাৎ অবতার হিসেবে গণ্য, আর-এক যাঁরা liberator হিসেবে গণ্য। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর একজন মহাপুরুষ।
৫.
আজকের সভায় আমি বিশেষভাবে রামমোহন রায়ের social consciousness এর পরিচয় দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। তবে তার ধর্মবুদ্ধির পরিচয় না দিলে তার সম্বন্ধে আলোচনা অঙ্গহীন হয় বলে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তার দার্শনিক মনোভাবের পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছি। কারও ছবি আঁকতে বসে তার মাথা বাদ দিয়ে দেহটি আঁকলে সে চিত্র যে পূর্ণাঙ্গ হয় না তা বলাই বাহুল্য।
রামমোহন রায় যখন যুবক তখন ইংরেজ এ দেশে একচ্ছত্র রাজা হয়ে বসেছেন। সমগ্র দেশ তখন ইংরেজের রাষ্ট্রনীতির অধীন হয়ে পড়েছে, আমাদের সমগ্র জীবনের উপর ইঙ্গ-সভ্যতার প্রভাব এসে পড়েছে। ইংরেজের শাসন ও ইংরেজি সভ্যতার প্রভাব যে আমাদের জাতীয় জীবনের মহা পরিবর্তন ঘটাবে, এ সত্য সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের চোখেই ধরা পড়ে। এই অতুলশক্তিশালী নবসভ্যতার সংঘর্ষে ভারতবাসীদের অন্ততঃ আত্মরক্ষার জন্যও সে সভ্যতার ধর্মকর্মের পরিচয় নেওয়াটা নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এই যুগসন্ধির মুখে একমাত্র রামমোহন রায়ের অন্তরে সমগ্র ভারতবর্ষ তার আত্মজ্ঞান লাভ করেছিল। রামমোহন এই মহাসত্য আবিষ্কার করেন যে, এই নবসভ্যতার সাহায্যে ভারতবাসী, শুধু আত্মরক্ষা নয়, স্বজাতির আত্মােন্নতি করতে পারবে। তাই জাতীয় আত্মোন্নতির যে পথ তিনি ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, অদ্যাবধি আমরা সেই পথ ধরে চলেছি। ইতিমধ্যে আর কেউ কোনো পথ আবিষ্কার করেছেন বলে তো আমার জানা নেই। যাকে সময়ে সময়ে আমরা নূতন পথে যাত্রা বলি, সে রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত মার্গে পিছু হটবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।
৬.
পৃথিবীতে যেসকল লোককে আমরা মহাপুরুষ বলি, তারা প্রত্যেকেই জাতীয় মন ও জাতীয় জীবনকে এমন একটা নতুন পথ ধরিয়ে দেন, যে পথ ধরে মানুষে মনে ও জীবনে অগ্রসর হয়। যে পথে অগ্রসর হয়ে অতীত ভারতবর্ষ বর্তমান ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছে সে পথের তিনিই হচ্ছেন সর্বপ্রথম দ্রষ্টা এবং প্রদর্শক। আমাদের জীবনে যে নবযুগ এসেছে তিনিই হচ্ছেন সে যুগের আবাহক।
ইংরেজের হাতে পড়ে আমাদের জীবনের ও মনের যে আমূল পরিবর্তন ঘটবে, ভারত-সভ্যতা যে নবকলেবর ধারণ করবে, এ সত্য সর্বাগ্রে রাজা রামমোহন রায়ের চোখেই ধরা পড়ে। সে যুগে তিনি ছিলেন একমাত্র লোক, যার অন্তরে ভারতের ভবিষ্যং সাকার হয়ে উঠেছিল। তাঁর সমসাময়িক অপরাপর বাংলা লেখকের লেখা পড়লে দেখা যায় যে, এক রামমোহন রায় ব্যতীত অপর কোনো বাঙালির এ চৈতন্য হয় নি যে, নবাবের রাজ্য কোম্পানির হাতে পড়ায় শুধু রাজার বদল হল না, সেই সঙ্গে জাতীয় জীবনের মহা পরিবর্তনের সূত্রপাত হল। ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এমন সব নবশক্তি এসে পড়ল যার সমবায়ে ও সংঘর্ষে ভারতবর্ষে একটি নূতন সমাজ ও নূতন সভ্যতা গঠিত হল। এবং সেসকল শক্তি যে কি এবং তার ভিতর কোন্ কোন্ শক্তি আমাদের জাতিগঠনের সহায় হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিকে দিব্যদৃষ্টি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, কেননা দেড় শ বৎসর ইংরেজের রাজ্যে বাস করে এবং প্রায় এক শ বৎসর ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেও আমাদের মধ্যে আজ খুব কম লোক আছেন, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ সম্বন্ধে যাদের ধারণা রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য স্পষ্ট। সম্যক্ জ্ঞানের অন্তরে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো ইতস্ততঃ নেই। সেই জ্ঞান কিন্তু শুধু স্কুলকলেজে বই পড়ে লাভ করা যায় না, ভগবদ্দত্ত প্রতিভা ব্যতীত কেউ আর যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন না। আপনারা মনে রাখবেন যে, রাজা রামমোহন ইংরেজের স্কুলকলেজে কখনো পড়েন নি, এবং ইংরেজি শিক্ষার সম্বল নিয়ে মনের দেশে যাত্রা শুরু করেন নি। সংস্কৃত আরবি ও ফারসি, এই তিন ভাষায় ও শাস্ত্রে শিক্ষিত মন নিয়েই তিনি ইংরেজি সভ্যতার দোষগুণ বিচার করতে বসেন এবং তার কোনো অংশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার কোনো কোনো শক্তিকে সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে অঙ্গীকার করেন।
৭.
জনরব এই যে, রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করে দেশের লোককে খৃস্টধর্মের আক্রমণ হতে রক্ষা করেছেন; সে আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি যে লেখনী ধারণ করেছিলেন সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। আমি নিম্নে তার একটি লেখা থেকে কতক অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তার থেকে আপনারা রামমোহন রায়ের মনের ও সেই সঙ্গে তার বাংলা রচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাবেন
শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানা বিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর। ও মোছলমানের ধৰ্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুংসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধৰ্ম্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশয় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কৰ্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রিষ্টের শিষ্যেরা স্বধৰ্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধৰ্ম্মের ঔৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধৰ্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধৰ্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুৰ্বল ও দীন ও ভয়ার্ল্ড প্রজার উপর ও তাঁহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধৰ্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধাম্মিক ব্যক্তিরা দুৰ্ব্বলের মনঃপীড়াতে সৰ্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুৰ্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাঁহার মর্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাণী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাঁহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধৰ্ম্ম জান ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব প্রকারে অনৈকতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে যখন এক দেশী লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদ স্বরূপ হয় তথাপি ঐ দুর্বল দেশীয়ের ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে… [ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১)]
যুক্তিযুক্ত ও সত্যমূলক হলে বিদ্রূপ যথেষ্ট ভদ্র হয়েও যে কতদূর সাংঘাতিক হতে পারে, উপরোক্ত বাক্য ক’টি তার একটি চমৎকার উদাহরণ। এই শ্রেণীর মারাত্মক বিপে রামমোহন রায় সিদ্ধহস্ত। বিপক্ষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে শিষ্টতা তিনি কখনো ত্যাগ করেন নি; কিন্তু ‘হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা’ তাঁর স্বভাব ও শিক্ষা দুয়েরই বিরুদ্ধে ছিল। প্রসিদ্ধ জর্মান কবি হাইনরিখ হাইনে Heinricli Heine বলে গিয়েছিলেন যে, তার গোরের উপর যেন এই ক’টি কথা লেখা থাকে যে, ‘He was a brave soldier in the war of liberation of humanity’–এ খ্যাতি রামমোহন রায় অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পারেন। মানুষের মুক্তির জন্য তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন। জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি অহিংসামূলক ধর্ম তার মনের উপর কখনো প্রভুত্ব করে নি, তিনি ছিলেন বেদপন্থী ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ রাজসিকতার মাহাত্ম্য তাঁর নিকট অবিদিত ছিল না। তামসিকতা যে অনেক স্থলে সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশ ধারণ করে, এ সত্যও তার সম্পূর্ণ জানা ছিল। আমরা, এ যুগের বাঙালি লেখকেরা, তাঁর কাছ থেকে একটি মহাশিক্ষা লাভ করতে পারি। তর্কক্ষেত্রে সৌজন্য রক্ষা করে কী করে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করা যায়, তার সন্ধান আমরা রামমোহন রায়ের লেখার ভিতর পাব, অবশ্য যদি আমরা সাহিত্যে একমাত্র বৈধহিংসার চর্চা করতে প্রস্তুত থাকি। যা অসত্য, যা অন্যায়, যা অবৈধ, তার পক্ষে যিনি লেখনী ধারণ করবেন তার গুরু রামমোহন রায় কখনোই হতে পারেন না। কেননা তার শাস্ত্রশাসিত মন অধর্মযুদ্ধের একান্ত প্রতিকূল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে রামমোহন রায় কিসের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেছিলেন। খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে নয়, কেননা কোনো ধর্মমতের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। তাঁর নিজের কথা এই–
… নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না তবে বিচার বলে হিন্দুর ধৰ্ম্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধৰ্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন সুতরাং ইচ্ছা পূৰ্ব্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম গ্রহণ করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধৰ্ম্ম সর্বদা ঐশ্বৰ্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমন নিয়ম নহে।… [ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১)]
অতএব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, তিনি এ দেশে খৃস্টধর্মের প্রচারের পদ্ধতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। কেননা উক্ত উপায়ে লোকের ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটানো সকল দেশেই উপদ্রববিশেষ এবং প্রবল রাজার জাতের পক্ষে দুর্বল প্রজার জাতের উপর এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অত্যাচার। রামমোহন রায় সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই নির্ভীক প্রতিবাদ করেছিলেন। যে যুগে ইংরেজের নামমাত্রে লোকে ভীত হত, সে যুগে ইংরেজের বিরুদ্ধে এই তীব্র প্রতিবাদ করায় তিনি যে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সাহস সকল দেশে সকল যুগেই দুর্লভ।
৮
আজকের দিনে যে মনোভাবকে আমরা জাতীয় আত্মমর্যাদাজ্ঞান বলি, রামমোহন রায়ের এই ক’টি কথায় তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িক অপর কোনো ব্যক্তির মনে এ মনোভাবের যে লেশমাত্র ছিল, তার কোনো নিদর্শন নেই। কিন্তু যেটা বিশেষ করে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মিছা আত্মশ্লাঘার নামগন্ধও নেই, অপর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মগ্লানিও আছে। সে যুগের বাঙালি যে দুর্বল ভয়ার্ত ও দীন ছিল সে কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, এবং কিসে স্বজাতির দুর্বলতা ভীরুতা ও দীনতা দূর করা যায় সেই ছিল তার একমাত্র ভাবনা, আর তার জাতীয় উন্নতি সাধনের সকল চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বজাতিকে মনে ও জীবনে শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যবান্ করে তোল। এই কথাটি মনে রাখলে তার সকল কথা সকল কার্যের প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতে পারি। তার পর স্বজাতিকে তিনি উন্নতির যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন সে পথ সুপথ কি কুপথ তার বিচার করতে হলে রামমোহন রায় কোন্ সত্যের উপর তার মতামতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।
পৃথিবীতে যেসকল লোকের মতামতের কোনো মূল্য আছে তাদের সকল মতামতের মধ্যে একটা সংগতি একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কেননা তাদের নানা বিষয়ে নানা জাতীয় মতের মূলে আছে একটি বিশেষ মানসপ্রকৃতি। রাজা রামমোহন রায় কি আধ্যাত্মিক, কি সাংসারিক, যে-কোনো বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন সেসকলের ভিতর দিয়ে তাঁর অসামান্য স্বাধীনতাপ্রিয়তা সদর্পে ফুটে বেরিয়েছে। তিনি যে বেদান্তের এত ভক্ত তার কারণ, ও-শাস্ত্র হচ্ছে মোক্ষশাস্ত্র। যে জ্ঞানের লক্ষ্য মুক্তি, ফল মুক্তি, সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করবার উপদেশ তিনি চিরজীবন স্বজাতিকে দিয়েছেন। এ মুক্তি কিসের হাত থেকে মুক্তি? এর দার্শনিক উত্তর হচ্ছে, অবিদ্যার হাত থেকে। এই অবিদ্যা বস্তু যে কি, সে বিষয়ে তর্কের আর শেষ নেই; ফলে অদ্যাবধি কেউ এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। অবিদ্যার মেটাফিজিক্যাল রহস্য ভেদ করবার বৃথা চেষ্টা না করেও সহজ বুদ্ধির সাহায্যে বোঝা যায়— বেদান্তের প্রতিপাদ্য মোক্ষ হচ্ছে ব্ৰহ্মবিষয়ক লৌকিক ধর্মের সংকীর্ণ ধারণা হতে মনের মুক্তি।
আপনারা সকলেই জানেন যে, বেদান্তশাস্ত্র নেতিমূলক। বেদান্তের ‘নেতি নেতি’র সার্থকতা সাধারণ লোকের ব্রহ্মবিষয়ক সকল অলীক ধারণার নিরাস করায়। এ বিষয়ে শংকরের মত তার মুখ থেকেই শোনা যাক। বেদান্তের চতুর্থ সূত্রের ভায্যের দুটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।
অস্যার্থ : তুমি তাহাকেই ব্ৰহ্ম বলিয়া জান যিনি ইদন্তারূপে (এই, অমুক) অথবা অন্য কোনো প্রকারে উপাসিত হন না।
ন হি শাস্ত্ৰমিদন্তয়া বিষয়ীভূতং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষতি।
অস্যার্থ : বেদান্তশাস্ত্র তাহাকে ইদন্তারূপে (কোনরূপ বিশেষণ দিয়া) প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছুক নহে। শাস্ত্র এইমাত্র প্রতিপাদন করে যে, ব্রহ্মপদার্থ ইদং জ্ঞানের অবিষয়।
বলা বাহুল্য, ধর্মজ্ঞানের রাজ্যে, এহেন মুক্তির বারতা পৃথিবীর অপর কোনো দেশে অপর কোনো শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এ মত কিন্তু নাস্তিক মত নয়, এ মত শুধু সকল প্রকার সংকীর্ণ আস্তিক মতের বিরোধী।
আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্যসভ্যতার চরম বাণী, সামাজিক সভ্যতা তেমনি বর্তমান ইউরোপীয় আর্যসভ্যতার চরম বাণী। এ সত্য আজকের দিনে আমাদের সকলেরই নিকট প্রত্যক্ষ, কেননা এ যুগের ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র যে কি, তা ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা সবাই জানি। কিন্তু এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির বহুপূর্বে, অর্থাৎ এক শ বৎসর পূর্বে, একমাত্র রামমোহন রায়ের চোখে এ সত্য ধরা পড়ে। ইউরোপের ঐ মহামন্ত্রই যে আমাদের যথার্থ সঞ্জীবনী মন্ত্র হবে, এই বিশ্বাসই ছিল তাঁর। সকল কথা সকল ব্যবহারের অটল ভিত্তি। তাই তিনি একদিকে যেমন ইউরোপের পৌরাণিক ধর্ম অগ্রাহ্য করেছিলেন, অপর দিকে তিনি তেমনি ইউরোপের সামাজিক ধর্ম সোৎসাহে সানন্দে অঙ্গীকার করেছিলেন। এই লিবার্টির ধর্মকেই আত্মসাৎ করে ভারতবাসী যে আবার নবজীবন নবশক্তি লাভ করবে এই সত্য প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের মহাব্রত।
৯.
লিবার্টি শব্দটা আজকের দিনে এত অসংখ্য লোকের মুখে মুখে ফিরছে, এক কথায় এতটা বাজারে হয়ে উঠেছে যে, ভয় হয় যে, অধিকাংশ লোকের মুখে ওটা একটা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। গীতার নিষ্কাম ধর্মের কথাটাকে আমরা যে একটা বুলিতে পরিণত করেছি, এ কথা তো আর সজ্ঞানে অস্বীকার করা চলে না। যে কথা মুখে আছে মনে নেই, যদিও বা মনে থাকে তো জীবনে নেই, তারই নাম না বুলি? অতএব এ স্থলে, বর্তমান ইউরোপ লিবার্টি শব্দের অর্থে কি বোঝে সে সম্বন্ধে বর্তমান ইতালির একজন অগ্রগণ্য লেখকের কথা এখানে বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি
প্রাচীনকালে লিবার্টি শব্দের অর্থে লোকে বুঝত শুধু দেশের গভর্নমেন্টকে নিজের করায়ত্ত করা। বর্তমানে লোকে লিবার্টি বলতে শুধু রাজনৈতিক নয়, সেই সঙ্গে মানসিক ও নৈতিক স্বাধীনতার কথাও বোঝে, অর্থাৎ এ যুগে লিবার্টির অর্থ, চিন্তা করবার স্বাধীনতা, কথা বলবার স্বাধীনতা, লেখবার স্বাধীনতা, নানা লোক একত্র হয়ে দল বাঁধবার স্বাধীনতা, বিচার করবার স্বাধীনতা, নিজের মত গড়বার এবং সে মত প্রকাশ করবার, প্রচার করবার স্বাধীনতা। মানুষমাত্রেই এসকল ক্ষেত্রে সমান স্বাধীনতার স্বভাবতই অধিকারী, এ স্বাধীনতা, কোনো চার্চ (ধর্মসংঘ) কর্তৃকও দত্ত নয়, কোনো রাজশক্তি কর্তৃকও দত্ত নয়। এর উলটো মত হচ্ছে এই যে, হয় ধর্মসংঘ নয় রাজশক্তি সর্বশক্তিমান, অতএব ব্যক্তির ব্যক্তিহিসেবে কোনোই স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র একটা জাতীয় সমূহের অন্তরে লীন হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়, সে সমূহ রাজাই হোক আর রাজ্যই হোক, চার্চই হোক আর পোপই হোক।
লেখকের মতে, যে দেশে যে সমাজে ব্যক্তিমাত্রেই এইসকল মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার অধিকারী নয়, সে দেশের লোমাত্রেই দাস; সে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা মিছা ও অর্থশূন্য। আমি ইচ্ছা করেই। De Sanctisএর মত আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, কেননা উক্ত লেখককে ইতালির রাজনৈতিক স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য আজীবন অশেষ অত্যাচার, বিশেষ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।
এ রাজা রামমোহন রায় লিবার্টি শব্দের এই নূতন অর্থ ই গ্রহণ করেছিলেন, এবং স্বজাতিকে মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দাসত্ব হতে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। লিবার্টির নূতন ধারণার ভিতর একটি দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে, সে তত্ত্ব এই যে, স্বাধীনতার মধ্যেই ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনীশক্তি স্ফুর্তি লাভ করে। এবং বহু লোকের মনে ও জীবনে এই শক্তি স্ফুর্ত হলেই জাতীয় জীবন যুগপৎ শক্তি ও উন্নতি লাভ করে। মানুষকে দাস রেখে মানবসমাজকে স্বাধীন করে তোলার যে কোনো অর্থ নেই এ জ্ঞান রামমোহন রায়ের ছিল, কেননা তিনি হেগেল প্রমুখ জর্মান দার্শনিকদের শিষ্য ছিলেন না।
১০
রামমোহন রায় জানতেন যে, তার স্বজাতি দুর্বল ভয়ার্ত ও দীন, এবং এরূপ হবার কারণ, সে জাতির নয় শ বছরের পূর্ব ইতিহাস এবং এই দুর্বল ভয়ার্ত ও দীন জাতির দুর্বলতা ভয় ও দৈন্য কি উপায়ে দূর করা যায়, এই ছিল তার জীবনের প্রধান ভাবনা। সুতরাং তাকে এক দিকে যেমন গভর্নমেন্টের আইনকানুনের দিকে নজর রাখতে হয়েছিল, অপর দিকে বাঙালির মানসিক ও সামাজিক মুক্তির উপায়ও নির্ধারণ করতে হয়েছিল।
ইংরেজিতে যাকে বলে civil and religious liberty, তার অভাবে কোনো জাতি যে মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায় না, এ সত্য তার কাছে স্পষ্ট ছিল। এই কারণে স্বজাতির সিভিল ও রিলিজিয়াস লিবার্টির রক্ষাকল্পে তখনকার ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জকে তিনি যে একখানি খোলাচিঠি লেখেন, সে পত্রে তিনি এতদূর স্বাধীন মনের পরিচয় দিয়েছিলেন যে, বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক বেন্থাম এ রচনাকে দ্বিতীয় Areopagatica স্বরূপে শিরোধার্য করেন। পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে এ পত্রখানি একখানি মহামূল্য দলিল। দুঃখের বিষয় এই যে, খুব কম বাঙালির এ দলিলখানির সঙ্গে পরিচয় আছে এবং একালের পলিটিশিয়ানদের মোটেই নেই। নেই যে, সেটি বড়ই আশ্চর্যের কথা, কেননা যে কংগ্রেস তাদের রাজনৈতিক ব্যবসার প্রধান সম্বল, সেই কংগ্রেসের মূল সূত্রগুলির স্থাপনা ১৮৩২ খৃস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ই করেন। অদ্যাবধি আমরা শুধু তার টীকাভাষ্যই করছি।
অধ্যাত্মিক দাসবুদ্ধির মত সামাজিক দাসবুদ্ধিরও মূলে আছে অবিদ্যা। আজকালের ভাষায় আমরা যাকে অজ্ঞতা বলি, শাস্ত্রের ভাষায় তাকে ব্যাবহারিক অবিদ্যা বলা যেতে পারে।
জাতীয় মনকে এই অবিদ্যার মোহ থেকে উদ্ধার করবার জন্য রামমোহন রায় এ দেশে ইউরোপীয় শিক্ষাকে আবাহন করে নিয়েছিলেন। যে জ্ঞান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু ছেরেপ কল্পনামূলক, সে জ্ঞান মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। রামমোহন রায় আবিষ্কার করেন যে, ইউরোপীয়দের অন্ততঃ দুটি শাস্ত্র আছে, সত্য যার ভিত্তি : এক বিজ্ঞান, আর-এক ইতিহাস। এই বিজ্ঞানের প্রসাদে এ বিশ্বের গঠন ও ক্রিয়ার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, আর এই ইতিহাসের কাছ থেকে মানবসমাজের উত্থান-পতন-পরিবর্তনের যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়; অন্ততঃ এ দুয়ের চর্চায় ফলে মানুষের মন মানুষ সম্বন্ধে ও বিশ্ব সম্বন্ধে ‘বড়াই বুড়ির কথা’র প্রভুত্ব হতে নিষ্কৃতি লাভ করে। যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন, অবিদ্যার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার নাম মুক্তিলাভ করা এবং মুক্তপুরুষই যথার্থ শক্তিমান্ পুরুষ। কিন্তু যথার্থ মুক্তি সাধনাসাপেক্ষ। রামমোহন রায় দেশের লোককে এই সত্যমূলক ইউরোপীয় শাস্ত্রমার্গে সাধনা করতে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। তারই ফলে বর্তমান ভারতবর্ষে বাঙালি জাতির স্থান সবার উপরে। কি সাহিত্যে, কি আর্টে, কি বিজ্ঞানে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, বাঙালি যে আজ ভারতবর্ষের সর্বাগ্রগণ্য জাতি, বাঙালির চিন্তা, বাঙালীর কর্ম আজ যে বাকি ভারতবর্ষের আদর্শ, বাঙালী যে এ যুগে মানসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষের যুগপৎ শিক্ষা ও দীক্ষা–গুরু, তার কারণ একটি বাঙালি মহাপুরুষের প্রদর্শিত মার্গে বাঙালির মন, বাঙালির জীবন আজ এক শ বৎসর ধরে অগ্রসর হয়েছে। এক কথায় আমাদের জাতীয় প্রতিভা রামমোহন রায়ের মনে ও জীবনে সম্পূর্ণ সাকার হয়ে উঠেছিল।
সুতরাং রামমোহন রায়ের মনে বাঙালি জাতি ইচ্ছা করলে তার নিজের মনের ছবি দেখতে পারে। বাঙালি জাতির মনে যেসকল শক্তি প্রচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিল, রামমোহন রায়ের অন্তরে সেইসকল শক্তি সংহত ও প্রকট হয়ে উঠেছিল। এর প্রমাণ রামমোহন রায়ের মন ও প্রকৃতি যদি অবাঙালি হত তাহলে আমরা পুরুষানুক্রমে কখনোই শিক্ষায় ও জীবনে অজ্ঞাতসারে তাঁর পদানুসরণ করতুম না।
এ কথাটা আজ স্বজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ বাঙালি যদি তার স্বধর্ম হারায় তাতে যে শুধু বাংলার ক্ষতি, তাই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেরও ক্ষতি। (আমরা যদি আমাদের মনের প্রদীপ জোর করে নেবাতে চেষ্টা করি, তাহলে যে ধূমের সৃষ্টি হবে তাতে সমস্ত ভারতবর্ষের মনের রাজ্য অন্ধকার হয়ে যাবে। একদল আত্মহারা বাঙালি আজকের দিনে স্বধর্ম বর্জন করতে উদ্যত হয়েছেন বলে রামমোহন রায়ের আত্মাকে স্বজাতির সুমুখে খাড়া করা অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করি।
১৩২৭ আশ্বিন
সনেট কেন চতুর্দশপদী
শ্ৰীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন গত মাসের ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় ‘সনেট-পঞ্চাশৎ’ নামক পুস্তিকার সমালোচনাসূত্রে সনেটের আকৃতি এবং প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় দিয়ে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ‘খুব সম্ভব কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষাদ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দশপদই সমীচীন এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।।
নানা যুগে নানা দেশে নানা কবির হাতে ফিরেও সনেট যে নিজের আকৃতি ও রূপ বজায় রাখতে পেরেছে, তার থেকে এই মাত্র প্রমাণ হয় যে, সনেটের ছাঁচে নানারূপ ভাবের মূর্তি ঢালাই করা চলে এবং সে ছাঁচ এতই টেকসই যে বড় বড় কবিদেরও ভাবের জোরে সেটি ভেঙেচুরে যায় নি। কিন্তু সনেট যে কেন চতুর্দশ পদ গ্রহণ করে জন্মলাভ করলে, সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। অথচ অস্বীকার করা যায় না যে, বারো কিংবা ষোলো না। হয়ে সনেটের পদসংখ্যা যে কেন চৌদ্দ হল তা জানবার ইচ্ছে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।
কি কারণে সনেট চতুর্দশপদী হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার একটি মত আছে এবং সে মত কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত; তার সপক্ষে কোনোরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতে আমি অপারগ। স্বদেশি কিংবা বিদেশি কোনোরূপ ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, পিঙ্গল কিংবা গৌর কোন আচার্যের পদসেবা আমি কখনো করি নি। সুতরাং আমার আবিষ্কৃত সনেটের ‘চতুর্দশীতত্ত্ব’ শাস্ত্রীয় কিংবা অশাস্ত্রীয়, তা শুধু বিশেষজ্ঞেরাই বলতে পারবেন।
চৌদ্দ কেন? এ প্রশ্ন সনেটের মত বাংলা পয়ার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। এর একটি সমস্যার মীমাংসা করতে পারলে অপরটির মীমাংসার পথে আমরা অনেকটা অগ্রসর হতে পারব।
আমার বিশ্বাস, বাংলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা চতুর্দশ হবার একমাত্র কারণ এই যে, বাংলা ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ হয় তিন অক্ষরের, নয় চার অক্ষরের। পাঁচ-ছয় অক্ষরের শব্দ প্রায়ই হয় সংস্কৃত নয়। বিদেশি। সুতরাং সাত অক্ষরের কমে সকল সময়ে দুটি শব্দের একত্র সমাবেশের সুবিধে হয় না। সেই সাতকে দ্বিগুণ করে নিলেই শ্লোকের প্রতি চরণ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচলিত শব্দই ঐ চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যেই খাপ খেয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের ভাষায় দু অক্ষরের শব্দের সংখ্যাও কিছু কম নয়। কিন্তু সেসকল শব্দকে চার অক্ষরের শব্দের শামিল ধরে নেওয়া যেতে পারে, যেহেতু দুই স্বভাবতঃই চারের অন্তভূত।
এই চৌদ্দ অক্ষর থাকবার দরুনই বাংলা ভাষায় কবিতা লেখবার পক্ষে পয়ারই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। একটানা লম্বা কিছু লিখতে হলে, অর্থাৎ যাতে অনেক কথা বলতে হবে এমন কোনো রচনা করতে গেলে, বাঙালি কবিদের পয়ারের আশ্রয় অবলম্বন ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কৃত্তিবাস থেকে আরম্ভ করে শ্ৰীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত বাংলার কাব্যনাটকরচয়িতামাত্রই পূর্বোক্ত কারণে অসংখ্য পয়ার লিখতে বাধ্য হয়েছেন, এবং চিরদিনের জন্য বাঙালির
প্রতিভা ঐ পয়ারের চরণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে।
পয়ারে চতুর্দশ অক্ষরের মত সনেটে চতুর্দশ পদের একত্র সংঘটন, আমার বিশ্বাস, অনেকটা একই কারণে একই রকমের যোগাযোগে সিদ্ধ হয়েছে।
বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, জীবজগৎ এবং কাব্যজগতের ক্রমোন্নতির নিয়ম পরস্পরবিরুদ্ধ। জীব উন্নতির সোপানে ওঠবার সঙ্গেসঙ্গেই তার ক্রমিক পদলোপ হয়, কিন্তু কবিতার উন্নতির সঙ্গেসঙ্গে পদবৃদ্ধি হয়। পদ্য দুটি চরণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে; দ্বিপদীই হচ্ছে সকল দেশে সকল ভাষার আদি ছন্দ। কলিযুগের ধর্মের মত, অর্থাৎ বকের মত, কবিতা একপায়ে দাঁড়াতে পারে না।
এই দ্বিপদী হতেই কাব্যজগতের উন্নতির দ্বিতীয় স্তরে ত্রিপদীর আবির্ভাব হয়, এবং ত্রিপদী কালক্রমে চতুষ্পদীতে পরিণত হয়। কবিতার পদবৃদ্ধির এই শেষ সীমা। কেন? সে কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। আমরা যখন মিল-প্রধান সনেটের গঠনরহস্য উদ্ঘাটন করতে বসেছি, তখন মিত্রাক্ষরযুক্ত দ্বিপদী ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর আকৃতির আলোচনা করাটাই আমাদের পক্ষে সংগত হবে। অমিত্রাক্ষর কবিতা কামচারী, চরণের সংখ্যাবিশেষের উপর তার কোনো নির্ভর নেই, তাই কোনোরূপ অঙ্কের ভিতর তাকে আবদ্ধ রাখবার জো নেই। ১দ্বিপদীর চরণ দুটি পাশাপাশি মিলে যায়। ত্রিপদীর প্রথম দুটি চরণ বিপদীর মত পাশাপাশি মেলে, তৃতীয় চরণটি অপর-একটি চরণের অভাবে আলগা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং অপর-একটি ত্রিপদীর সান্নিধ্যলাভ করলে তার তৃতীয় চরণের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়। বাংলা সংস্কৃত ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষার ত্রিপদীর আকৃতি ও প্রকৃতি এইরূপ, কিন্তু ইতালীয় ত্রিপদীর (terza rima) গঠন স্বতন্ত্র।
ইতালীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের সহিত তৃতীয় চরণের মিল হয়, এবং দ্বিতীয় চরণ মিলের জন্য পরবর্তী ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে। ইতালীয় ত্রিপদী তিন চরণেই সম্পূর্ণ। ভাব এবং অর্থ বিষয়ে একটির সহিত অপরটি পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন। পূর্বাপরযোগ কেবলমাত্র মিলসূত্রে রক্ষিত হয়। একটি কবিতার ভিতর, তা যতই বড় হোক-না কেন, সে যোগের কোথাও বিচ্ছেদ নেই। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একটি কবিতার অন্তভূত ত্রিপদীগুলি এই মিলনসূত্রে গ্রথিত, এবং ইঙ্কুর পাকের ন্যায় পরস্পরযুক্ত। নিম্নে রবার্ট ব্রাউনিং রচিত ‘THE STATUE AND THE BUST নামক কবিতা হতে ইতালীয় ত্রিপদীর নমুনাস্বরূপ ছয়টি চরণ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। পাঠক দেখতে পাবেন যে, প্রথম ত্রিপদীর মধ্যম চরণটি মিলের জন্য দ্বিতীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে।
There’s a palace in Florence, the world knows well,
And a statue watches it from the square,
And this story of both do our towusmen tell,
Ages ago, a lady there,
At the farthest window facing the East
Asked, ‘Who rides by with the royal air?
অর্থাৎ ত্রিপদীর বিশেষত্ব হচ্ছে, দুটি চরণ পাশাপাশি না মিলে মধ্যস্থ একটি কিংবা দুটি চরণ ডিঙিয়ে মেলে। ত্রিপদীর এই মিলের ক্ষণিক বিচ্ছেদ রক্ষা করে চারটি চরণের মধ্যে দু-জোড়া মিলকে স্থান দেবার ইচ্ছে থেকেই চতুষ্পদীর জন্ম। দুটি দ্বিপদী পাশাপাশি বসিয়ে দিলে চতুষ্পদী হয় না। চতুষ্পদীতে প্রথম চরণ হয় তৃতীয় চরণের সঙ্গে নয় চতুর্থ চরণের সঙ্গে মেলে, আর দ্বিতীয় চরণ হয় তৃতীয় নয় চতুর্থের সঙ্গে মেলে। এক কথায় চতুষ্পদীর আকৃতি দ্বিপদীর এবং প্রকৃতি ত্রিপদীর।
আমি পূর্বেই বলেছি যে, দ্বিপদী ত্রিপদী ও চতুষ্পদীই পদ্যের মূল উপাদান। বাদবাকি যত প্রকার পদ্যের আকার দেখতে পাওয়া যায়, সে সবই দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদীকে হয় ভাঙচুর করে নয় জোড়াতাড় দিয়ে গড়া। এ সত্য প্রমাণ করবার জন্য বোধ হয় উদাহরণ দেবার আবশ্যক নেই।
কবিতার পূর্ববর্ণিত ত্রিমূর্তির সমন্বয়ে একমূর্তি গড়বার ইচ্ছে থেকেই সনেটের সৃষ্টি। সেই কারণেই সনেট আকৃতিতে সমগ্ৰতা একাগ্রতা এবং সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ত্রিপদীর সঙ্গে চতুষ্পদীর যোগ করলে সপ্ত পদ পাওয়া যায়, এবং সেই সপ্ত পদকে দ্বিগুণিত করে নেওয়াতেই সনেট চতুর্দশ পদ লাভ করেছে। এই চতুর্দশ পদের ভিতর দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী তিনটিরই স্থান আছে, এবং তিনটিই সমান খাপ খেয়ে যায়।
পেত্রার্কার সনেটের অষ্টক পরস্পর মিলিত এবং একাঙ্গীভূত দুটি যমজ চতুষ্পদীর সমষ্টি; এবং প্রতি চতুষ্পদীর অভ্যন্তরে একটি করে আস্ত দ্বিপদী বিদ্যমান। ষষ্ঠকও ঐরূপ দুটি ত্রিপদীর সমষ্টি। ফরাসি সনেটও ঐ একই নিয়মে গঠিত, উভয়ের ভিতর পার্থক্য শুধু ষষ্ঠকের মিলের বিশিষ্টতায়। ফরাসি ভাষায় ইতালীয় ভাষার ন্যায় পদে পদে ছত্রব্যবধান দিয়ে চরণে চরণে মিলনসাধন করা স্বাভাবিক নয়; সেইজন্য ফরাসি সনেটে যষ্ঠকের প্রথম দুই চরণ দ্বিপদীর আকার ধারণ করে।
সনেট ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর যোগে ও গুণে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে চতুর্দশপদী হতে বাধ্য।
১৩২০ ভাদ্র
সবুজ পত্রের মুখপত্র
ওঁ প্ৰাণায় স্বাহা
স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙালি জাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, একটা নতুন কিছু করো। সেই পরামর্শ অনুসারেই যে আমরা একখানি নতুন মাসিক পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এ পৃথিবীটি যথেষ্ট পুরোনো, সুতরাং তাকে নিয়ে নতুন কিছু করা বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ এ দেশে। যদি বহু চেষ্টায় নতুন কিছু করে তোলা যায়, তা হয় জলবায়ুর গুণে দু দিনেই পুরোনো হয়ে যায়, নয় তো পুরাতন এসে তাকে গ্রাস করে ফেলে। এইসব দেখেশুনে এ দেশে কথায় কিংবা কাজে নতুন কিছু করবার জন্য যে পরিমাণ ভরসা ও সাহস চাই তা যে আমাদের আছে তা বলতে পারি নে।।
যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, তবে কি উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য, কি অভাব পূরণ করবার জন্য, এত কাগজ থাকতে আবার একটি নতুন কাগজ বার করছি–তাহলেও আমাদের নিরুত্তর থাকতে হবে; কেননা কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারাটা সাহিত্যসমাজেও ভদ্রতার পরিচায়ক নয়। নিজেকে প্রকাশ করবার পূর্বে নিজের পরিচয় দেওয়াটা শুধু পরিচয় দেওয়া নয়, নিজের গুণগ্রাম বর্ণনা করাটা যদিও মাসিক পত্রের পক্ষে একটা সর্বলোকমান্য ‘সাহিত্যিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও সে নিয়ম ভঙ্গ করতে আমরা বাধ্য। যে কথা বারো মাসে বারো কিস্তিতে রাখতে হবে, তার যে মাঝে মাঝে খেলাপ হবার সম্ভাবনা নেই— এ জাক করবার মত দুঃসাহস আমাদের নেই। তাছাড়া স্বদেশের কিংবা স্বজাতির কোনো-একটি অভাব পূরণ করা, কোনো-একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয় ধর্মও নয়; সে হচ্ছে কার্যক্ষেত্রের কথা। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করাতে মনের ভিতর যে সংকীর্ণতা এসে পড়ে, সাহিত্যের স্মৃতির পক্ষে তা অনুকূল নয়। কাজ হচ্ছে দশে মিলে করবার জিনিস। দলবদ্ধ হয়ে আমরা সাহিত্য গড়তে পারি নে, গড়তে পারি শুধু সাহিত্যসম্মিলন। কারণ দশের সাহায্য ও সাহচর্যে কোন কাজ উদ্ধার করতে হলে নিজের স্বাতন্ত্রটি অনেকটা চেপে দিতে হয়। যদি আমাদের দশজনের মধ্যে মনের চৌদ্দআনা মিগ থাকে, তাহলে প্রতিজনে বাকি কুলানা বাদ দিয়ে, একত্র হয়ে সকলের পক্ষে সমান বাছিত কোনো ফললাভের জন্য চেষ্টা করতে পারি। এক দেশের এক যুগের এক সমাজের বহু লোকের ভিতর মনের এই চৌদ্দআনা মিল থাকলেই সামাজিক কার্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়, নচেৎ নয়। কিন্তু সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের ঐ পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দআনার চাইতে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব, দুআনার মূল্য ঢের বেশি। কেননা ঐ দুআনা হতেই তার সৃষ্টি এবং স্থিতি, বাকি চৌদ্দআনায় তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোলোআনা মনের মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে। এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য সকল দর্শন সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।
এ কথা শুনে অনেকে হয়ত বলবেন যে, যে দেশে এত দিকে এত অভাব সে দেশে যে লেখা তার একটি অভাব পূরণ না করতে পারে, সে লেখা সাহিত্য নয়-শখ; ও তো কল্পনার আকাশে রঙিন কাগজের ঘুড়ি ওড়ানো, এবং সে ঘুড়ি যত শীঘ্র কাটা পড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ততই ভালো। অবশ্য ঘুড়ি। ওড়াবারও একটা সার্থকতা আছে। ঘুড়ি মানুষকে অন্ততঃ উপরের দিকে চেয়ে দেখতে শেখায়। তবুও এ কথা সত্য যে, মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনো কথায় চিড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো-কোনো কথায় মন ভেজে; এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের শক্তি অপরিসীম। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মশার গুন্গুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায় অবশ্য যদি মশারির ভিতর শোওয়া যায়; আর দিনের আলোর সঙ্গে কাক-কোকিলের ডাক মানুষকে জাগিয়ে তোলে। প্রাণ পদার্থটির গূঢ় তত্ত্ব আমরা না জানলেও তার প্রধান লক্ষণটি এতই ব্যক্ত এবং এতই স্পষ্ট যে তা সকলেই জানেন। সে হচ্ছে তার জাগ্রত ভাব। অপরদিকে নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর সহোদরা। কথায় হয় আমাদের জাগিয়ে তোলে, নয় ঘুম পাড়িয়ে দেয় তাই আমরা কথায় মরি কথায় বাঁচি। মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কি না জানি নে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। মানুষমাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানি নে, কেননা জানি নে। সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখিরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্ৰমণ্ডিত সাহিত্যের নবশাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন তাহলে আমরা বাঙালি জাতির সবচেয়ে যে বড় অভাব, তা কতকটা দূর করতে পারব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারই জ্ঞান। আমরা যে, আমাদের সে অভাব সম্যক উপলব্ধি করতে পারি নি তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্যকে ঔদাস্য বলে, শ্মশানবৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব বলে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য, আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।
আমরা যে দেশের মনকে ঈষৎ জাগিয়ে তুলতে পারব, এত বড় স্পর্ধার কথা আমি বলতে পারি নে, কেননা যে সাহিত্যের দ্বারা তা সিদ্ধ হয়, সে সাহিত্য গড়বার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়–তার মূলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই অর্থাৎ নৈসর্গিকী প্রতিভা থাকা চাই। অথচ ও ঐশ্বর্য ভিক্ষা করে পাবার জিনিস নয়। তবে বাংলার মন যাতে আর বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে, সে ক্ষমতার প্রয়োগটি কেবল আমাদের প্রবৃত্তিসাপেক্ষ। এবং আমাদের প্রবৃত্তির সহজ গতিটি যে ঐ নিজেকে এবং অপরকে সজাগ করে তোলবার দিকে, তাও অস্বীকার করবার জো নেই। কারণ ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের সাহিত্য ইউরোপের দর্শন মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক মদিরাই হোক আর হলাহলই হোক, তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে, আমরা দেশসুদ্ধ লোক যেদিকে, হোক কোনো-একটা দিকে চলবার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আঁকুবাঁকু করছি। কেউ পশ্চিমের দিকে এগোতে চান কেউ পূর্বের দিকে পিছু হটতে। চান, কেউ আকাশের উপরে দেবতার আত্মার অনুসন্ধান করছেন কেউ মাটির নীচে দেবতার মূর্তির অনুসন্ধান করছেন। এক কথায়, আমরা উন্নতিশীলই হই আর অবনতিশীলই হই আমরা সকলেই গতিশীল, কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর-কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ হতেই আমাদের নবসাহিত্যের সৃষ্টি। সুন্দরের আগমনে হীরা মালিনীর ভাঙা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটে উঠেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে। তার ফল কি হবে সে কথা না বলতে পারলেও এই ফুলফোঁটা যে বন্ধ করা উচিত নয়, এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন। তাঁকেই আমরা ফুলের চাষ করবার জন্য উৎসাহ দেব।
ইউরোপের কাছে আমরা একটি অপূর্ব জ্ঞান লাভ করেছি। সে হচ্ছে এই যে, ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আনো-না কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ করতে হবে। চীনের টবে তোলা-মাটিতে সে বীজ বপন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমাদের এই নবশিক্ষাই ভারতবর্ষের অতিবিস্তৃত অতীতের মধ্যে আমাদের এই নবভাবের চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র চিনে নিতে শিখিয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার গুণেই আমরা দেশের লুপ্ত অতীতের পুনরুদ্ধারকল্পে ব্ৰতী হয়েছি। তাই আমাদের মন একলম্ফে শুধু বঙ্গ-বিহার নয়, সেইসঙ্গে হাজার দেড়েক বৎসর ডিঙিয়ে একেবারে আর্যাবর্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখন আমাদের পূর্ব কবি হচ্ছে কালিদাস, কাশীদাস নয়; দার্শনিক শংকর, গদাধর নয়; শাস্ত্রকার মনু, রঘুনন্দন নয়; আলংকারিক দণ্ডী, বিশ্বনাথ নয়। নব্যন্যায় নব্যদর্শন নব্যস্মৃতি আমাদের কাছে এখন অতিপুরাতন। আর যা কালের হিসাবে অতিপুরাতন, তাই আবার বর্তমানে নতুন রূপ ধারণ করে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে ইউরোপের নবীন সাহিত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের আকারগত সাদৃশ্য না থাকলেও অন্তরের মিল আছে। সে হচ্ছে প্রাণের মিল –উভয়ই প্রাণবন্ত। গাছের গোলাপের সঙ্গে কাগজের গোলাপের সাদৃশ্য থাকলেও জীবিত ও মৃতের ভিতর যে পার্থক্য, উভয়ের মধ্যে সেই পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু স্থলের গোলাপ ও জলের পদ্ম উভয়ে একজাতীয়, কেননা উভয়েই জীবন্ত। সুতরাং আমাদের নবজীবনের নবশিক্ষা, দেশের দিক ও বিদেশের দিক দুই দিক থেকেই আমাদের সহায়। এই নবজীবন যে লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই লেখাই কেবল সাহিত্য বাদবাকি লেখা কাজের নয়, বাজে।
এই সাহিত্যের বহির্ভূত লেখা আমাদের কাগজ থেকে বহিভূত করবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছি বলে আমরা এই নতুন পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি। একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালির জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য।
এই নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সাহিত্য যে কেন পুষ্পিত না হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠছে, তার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নয়। কিঞ্চিং বাহদৃষ্টি এবং কিঞ্চিৎ অন্তদৃষ্টি থাকলেই সে কারণের দুই পিঠই সহজে মানুষের চোখে পড়ে।
সাহিত্য এ দেশে অদ্যাবধি ব্যাবসাবাণিজ্যের অঙ্গ হয়ে ওঠে নি। তার জন্য দোষী লেখক কি পাঠক, বলা কঠিন। ফলে আমরা হচ্ছি সব সাহিত্যসমাজের শখের কবির দল। অব্যবসায়ীর হাতে পৃথিবীর কোনো কাজই যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না, এ কথা সৰ্বলোকস্বীকৃত। লেখা আমাদের অধিকাংশ লেখকের পক্ষে কাজও নয় খেলাও নয়, শুধু অকাজ; কারণ খেলার ভিতর যে। স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা আছে, লেখায় তা নেই; অপরদিকে কাজের ভিতর যে যত্ন ও মন আছে, তাও তাতে নেই। আমাদের রচনার মধ্যে অন্যমনস্কতার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়; কেননা যে অবসর আমাদের নেই, সেই অবসরে আমরা সাহিত্যরচনা করি। আমরা অবলীলাক্রমে সাহিত্য গড়তে চাই বলে আমাদের নৈসর্গিকী প্রতিভার উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই। অথচ এ কথা লেখকমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, যিনি সরস্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করে লেখেন, সরস্বতী চাই-কি তার প্রতি অনুগ্ৰহ নাও করতে পারেন। এই একটি কারণ যার জন্যে বঙ্গসাহিত্য পুষ্পিত না হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠছে। ফুলের চাষ করতে হয়, জঙ্গল আপনি হয়। অতিকায় মাসিক পত্রগুলি সংখ্যাপুরণের জন্য এই আগাছার অঙ্গীকার করতে বাধ্য, এবং সেই কারণে আগাছার বৃদ্ধির প্রশ্রয় দিতেও বাধ্য। এইসব দেখেশুনে ভয়ে সংকুচিত হয়ে আমাদের কাগজ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে। এই আকারের ভারতম্যে প্রকারেরও কিঞ্চিৎ তারতম্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমাদের স্বল্পায়তন, ত্রে অনেক লেখা আমরা অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হব। স্ত্রীপাঠ্য শিশুপাঠ্য স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য প্রবন্ধসকল অনাহুত কিংবা রবাহুত হয়ে আমাদের দ্বারস্থ হলেও আমরা তাদের স্বস্থানে প্রস্থান করতে বলতে পারব। কারণ আমাদের ঘরে স্থানাভাব। এক কথায়, শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমাদের প্রকাশ করতে হবে না। এর লাভ যে কি, তিনিই বুঝতে পারবেন যিনি জানেন যে, যে কথা এক শ বার বলা হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি করাই শিক্ষকের ধর্ম ও কর্ম। যে লেখায় লেখকের মনের ছাপ নেই, তা ছাপালে সাহিত্য হয় না।
তার পর, যে জীবনীশক্তির আবির্ভাবের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, সে শক্তি আমাদের নিজের ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ হয় নি; তা হয় দূর দেশ হতে নয় দূর কাল হতে, অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছে। সে শক্তি এখনো আমাদের সমাজে ও মনে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। সে শক্তিকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে না পারলে তার সাহায্যে আমরা সাহিত্যে ফুল কিংবা জীবনে ফল পাব না। এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাবসকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের। সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনো বাইরের নিয়ম চাই নে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখায় সংযত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া। আমাদের কাগজে আমরা তাই সেই সীমা নির্দিষ্ট করে দেবার চেষ্টা করব।
আমার শেষ কথা এই যে, যে শিক্ষার গুণে দেশে নূতন প্রাণ এসেছে, মনে সাহিত্য গড়বার প্রবৃত্তি জন্মিয়ে দিয়েছে, সেই শিক্ষার দোষেই সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করবার অনুরূপ ক্ষমতা আমরা পাই নি। আমরা বর্তমান ইউরোপ ও অতীত ভারতবর্ষ, এ উভয়ের দোটানায় পড়ে বাংলা প্রায় ভুলে গেছি। আমরা শিখি ইংরেজি, লিখি বাংলা, মধ্যে থাকে সংস্কৃতের ব্যবধান। ইংরেজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও তার চারা তুলে বাংলার মাটিতে বসাতে হবে, নইলে স্বদেশি সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই মেঘনাদবধকাব্য পরগাছার ফুল। অর্কিড’এর মত তার আকারের অপূর্বত এবং বর্ণের গৌরব থাকলেও তার সৌরভ নেই। খাঁটি স্বদেশি বলে অন্নদামঙ্গল স্বল্পপ্রাণ হলেও কাব্য; এবং কোনো দেশেরই নয়। বলে বৃত্রসংহার মহাপ্রাণ হলেও মহাকাব্য নয়। ভারতচন্দ্র ভাষার ও ভাবের একতার গুণে সংযমের গুণে তার মনের কথা ফুলের মত সাকার করে তুলেছেন, এবং সে ফুলে, যতই ক্ষীণ হোক-না কেন, প্রাণও আছে গন্ধও আছে। দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি বাংলার পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ করলেই তাতে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। তার জন্য আবশ্যক আর্ট, কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য। আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা, আশা করি, এ বিষয়ে লেখকদের সহায়তা করবে। বড়কে ছোটর ভিতর ধরে রাখাই হচ্ছে আর্টের উদ্দেশ্য। ওস্তাদরা বলে থাকেন যে গৌড়সারঙ্গ রাগিণী ঘোট, কিন্তু গাওয়া মুশকিল; ‘ছোটিসে দরওয়াজাকে অন্দর হাতি নিকানা যৈসা মুশকিল ঐসা মুশকিল, দরিয়াকে পাকড়কে কুঁজামে ডানা যৈসা মুশকিল ঐসা মুশকিল। অবস্থা গুণে যতই মুশকিল হোক-না কেন, বাঙালি জাতিকে এই গৌড়সারঙ্গই গাইতে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের বাংলাঘরের খিড়কিদরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতি গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড়ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করতে চেষ্টা করতে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোনো সহজ সাধনপদ্ধতি আমাদের জানা নেই।
১৩২১ বৈশাখ
সবুজপত্র
বাংলাদেশ যে সবুজ, একথা বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য লোকেও অস্বীকার করবেন না। মা’র শস্যশ্যামলরপ বাংলার এত গদ্যেপদ্যে এতটা পল্লবিত হয়ে উঠেছে যে, সে বর্ণনার যাথার্থ বিবাস করবার জন্য চোখে দেখবারও আবশ্যক। নেই। পনেরক্তির গুণে এটি সেই শ্রেণীর সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার সম্বন্ধে চক্ষুকণের যে বিবাদ হতে পারে, এরূপ সন্দেহ আমাদের মনে মহতের জন্যও স্থান পায় না। এক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশত নাম ও রূপের বাস্তবিকই কোনো বিরোধ নেই। একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, তরাই হতে সুন্দরবন পর্যন্ত এক ঢালা সবুজবৰ্ণ দেশটিকে আদ্যোপান্ত ছেয়ে রেখেছে। কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কোথাও তার বিরাম নেই। শুধু তাই নয়, সেই রং বাংলার সীমানা অতিক্রম করে উত্তরে হিমালয়ের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ভিতর চারিয়ে গেছে।
সবুজ, বাংলার শুধু, দেশজোড়া রং নয়–বারোমেসে রং। আমাদের দেশে প্রকৃতি বহুরূপী নয়, এবং ঋতুর সঙ্গেসঙ্গে বেশ পরিবর্তন করে না। বসন্তে বিয়ের কনের মত ফলের জহরতে আপাদমস্তক সালংকারা হয়ে দেখা দেয় না, বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হয়ে শরতের পূজার তসর ধারণ করে আসে না, শীতে বিধবার মত শাদা শাড়িও পরে না। মাধব হতে মধ পর্যন্ত ঐ সবুজের টানা সুর চলে; ঋতুর প্রভাবে সে সুরের যে রূপান্তর হয়, সে শুধু কড়িকোমলে। আমাদের দেশে অবশ্য বর্ণের বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আকাশে ও জলে, ফলে ও ফলে আমরা বর্ণগ্রামের সকল সুরেরই খেলা দেখতে পাই। কিন্তু মেঘের রং ও ফলের রং ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃতির ওসকল রাগরঙ্গ তার বিভাব ও অভাব মাত্র। তার স্থায়ী ভাবের, তার মূল রসের পরিচয় শুধু সবজে। পাঁচরঙা ব্যাভিচারীভাবসকলের সার্থকতা হচ্ছে বঙ্গদেশের এই অখণ্ডহরিৎ স্থায়ী ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা।
এরূপ হবার অবশ্য একটা অর্থ আছে। বর্ণমাত্রেই ব্যঞ্জন বর্ণ; অর্থাৎ বর্ণের উদ্দেশ্য শুধু বাহ্যবস্তুকে লক্ষণান্বিত করা নয়, কিন্তু সেই সুযোগে নিজেকেও ব্যক্ত করা। যা প্রকাশ নয়, তা অপর কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। তাই রং রূপও বটে, রূপকও বটে। যতক্ষণ আমাদের বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ ব্যক্তিত্বের জ্ঞান না জন্মায়, ততক্ষণ আমাদের প্রকৃতির বর্ণপরিচয় হয় না এবং আমরা তার বক্তব্য কথা বুঝতে পারি নে। বাংলার সবুজপত্রে যে সুসমাচার লেখা আছে, তা পড়বার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক হবার আবশ্যক নেই। কারণ সে লেখার ভাষা বাংলার প্রাকৃত। তবে আমরা সকলে যে তার অর্থ বুঝতে পারি নে, তার কারণ হচ্ছে যিনি গুপ্ত জিনিস আবিষ্কার করতে ব্যস্ত, ব্যক্ত জিনিস তাঁর চোখে পড়ে না।
যাঁর ইন্দ্রধনুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে আর তার জন্মকথা জানা আছে, তিনিই জানেন যে, সূর্যকিরণ নানা বর্ণের একটি সমন্টিমাত্র এবং শুধু সিধে পথেই সে শাদা ভাবে চলতে পারে। কিন্তু তার সরল গতিতে বাধা পড়লেই সে সমষ্টি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বক্র হয়ে বিচিত্র ভঙ্গি ধারণ করে, এবং তার বর্ণসকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত হয়ে যায়। সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি, এবং নিজগুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে; বেগুনি কিশলয়ের রং, জীবনের পরাগের রং; লাল রক্তের রং, জীবনের পর্ণেরাগের রং; নীল আকাশের রং, অনন্তের রং; পীত শপত্রের রং, মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং, রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি; তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পবসীমায় বেগুনি আর পশ্চিমসীমায় লাল। অত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্বে ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবরে, অর্থাৎ সরস প্রাণের, স্বধর্ম।
যে বর্ণ বাংলার ওষধিতে ও বনতিতে নিত্য বিকশিত হয়ে উঠছে, নিশ্চয় সেই একই বর্ণ আমাদের হদয়-মনকেও রঙিয়ে রেখেছে। আমাদের বাহিরের প্রকৃতির যে রং, আমাদের অন্তরের পুরুষেরও সেই রং। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে সজীবতা ও সরসতই হচ্ছে বাঙালির মনের নৈসর্গিক ধর্ম। প্রমাণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, আমাদেব দেবতা হয় শ্যাম নয় শ্যামা। আমাদের হদয়মন্দিরে রজতগিরিসভি কিংTI জবাকুসুমসংকাশ দেবতার স্থান নেই; আমরা শৈবও নই, সৌরও নই।
আমরা হয় বৈষ্ণব, নয় শাক্ত। এ উভয়ের মধ্যে বাঁশি ও অসির যা প্রভেদ, সেই পার্থক্য বিদ্যমান; তবও বর্ণসামান্যতার গুণে শ্যাম ও শ্যামা আমাদের মনের ঘরে নির্বিবাদে পাশাপাশি অবস্থিতি করে। তবে বঙ্গসরস্বতীর দবাদলশ্যামরপ আমাদের চোখে যে পড়ে না, তার জন্য দোষী আমরা নই, দোষী আমাদের শিক্ষা। একালের বাণীর মন্দির হচ্ছে বিদ্যালয়। সেখানে আমাদের গররা এবং গরজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণমতির প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমাদের মন তার কায়িক এবং বাচিক সেবায় দিন-দিন নীরস ও নিজীব হয়ে পড়ছে। আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করি নে, তার কারণ আমাদের নিজের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শাধ একজনকে আর-পাঁচজনের মত হতে বলে, ভুলেও কখনো আর-পাঁচজনকে একজনের মত হতে বলে না। সমাজের ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম নষ্ট করা। সমাজের যা মন্ত্র, তারই সাধনপদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে ‘অপরের মত হও’, আর তার নিষেধ হচ্ছে নিজের মত হয়ো না। এই শিক্ষার কৃপায় আমাদের মনে এই অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আমাদের স্বধর্ম এতই ভয়াবহ যে তার চাইতে পরধর্মে নিধনও শ্রেয়। সুতরাং কাজে ও কথায়, লেখায় ও পড়ায়, আমরা আমাদের মনের সরস সতেজ ভাবটি নষ্ট করতে সদাই উৎসুক। এর কারণও স্পষ্ট, সবুজ রং ভালোমন্দ দুই অর্থেই কাঁচা। তাই আমাদের কর্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীর দল, আমাদের মনটিকে রাতারাতি পাকা করে তুলতে চান। তাঁদের বিশ্বাস যে, কোনোরূপ কর্ম কিংবা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেলতে পারলেই আমাদের মনের রং পেকে উঠবে। তাঁদের রাগ এই যে, সবুজ বর্ণমালার অন্তস্থ বর্ণ নয়, এবং ও রং কিছুরই অতে আসে না জীবনেরও নয়, বেদেরও নয়, কমেরও নয়, জ্ঞানেরও নয়। এদের চোখে সবুজ মনের প্রধান দোষ যে, সে মন পর্বমীমাংসার অধিকার ছাড়িয়ে এসেছে এবং উত্তরমীমাংসার দেশে গিয়ে পৌঁছয় নি। এরা ভুলে যান যে, জোর করে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি, প্রাণকে মৃত্যুর দ্বারস্থ করি। অপরদিকে এদেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান। এরা চান যে, আমরা শুধু গদগদভাবে আধ-আধ কথা কই। এদের রাগ সবুজের সজীবতার উপর। এদের ইচ্ছা, সবুজের তেজক বহিস্কৃত করে দিয়ে ছাঁকা রসটকু রাখেন। এরা ভুলে যান যে, পাতা কখনো আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না। প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না; তার ধর্ম হচ্ছে এগনো, তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কমের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই কেবলমাত্র ভক্তির শান্তিজলে সে তার সমস্ত হদয় পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এ উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বাঙালির মন এখন অর্ধেক অকালপক্ক, এবং অর্ধেক অযথা-কচি। আমাদের আশা আছে যে, সবুজ ক্ৰমে পেকে লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের অন্তরের আজকের সবুজরস কালকের লালরক্তে তবেই পরিণত হবে, যদি আমরা স্বধর্মের পরিচয় পাই, এবং প্রাণপণে তার চর্চা করি। আমরা তাই দেশী কি বিলেতি পাথরে-গড়া সরস্বতীর মতির পরিবর্তে বাংলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘট স্থাপনা করে তার মধ্যে সবজেপত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোনো গভমন্দির থাকবে না, কারণ সবুজের পর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়; বন্ধ ঘরে সবুজ দঃখে পাণ্ডু হয়ে যায়। আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গেসঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। উষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীললোহিত, বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজপত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যতি কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল করে তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্কপত্রের।
বৈশাখ ১৩২১
সাহিত্যসম্মিলন
গত সাহিত্যসম্মিলনে একটি নূতন সুরের পরিচয় পাওয়া গেছে—সে হচ্ছে সত্যের সুর। এ সুর যে বঙ্গসাহিত্যে পূর্বে কখনো শোনা যায় নি, তা নয়। তবে নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে, আর-পাঁচটি বিবাদী সংবাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে এবারকার পালায় এইটিই ছিল স্থায়ী সুর। এবং সে সুর যে অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার কারণ তা কোমল নয়, তীব্র।
এবারকার ব্যাপারের কর্মকর্তারা নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সাহিত্যিকদের প্রচলিত প্রথামত ‘আসুন বসুন’ বলে সম্ভাষণ করেন নি, ‘উঠুন চলুন বলে অভিভাষণ করেছেন। এরা সকলেই গলার আওয়াজ আধ-সুর চড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে একবাক্যে বলেছেন যে, এ দেশের সেকাল সত্যযুগ হতে পারে, কিন্তু একাল হচ্ছে মিথ্যার যুগ। এই দেশব্যাপী মিথ্যার হাত হতে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়, তারই সন্ধান বলে দেওয়াটাই ছিল সাহিত্যাচার্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য।
মিথ্যার চর্চা লোকে দুভাবে করে এক জেনে, আর-এক না জেনে। সত্য যে কি, তা জেনেও কেউ কেউ কথায় ও কাজে তা নিত্য উপেক্ষা করেন। এ রোগের ঔষধ কি, বলা কঠিন; অন্ততঃ ওর কোনো টোটকা আমার জানা নেই। অপর পক্ষে, অনেকে কেবলমাত্র মানসিক জড়তাবশতঃ ও-বস্তু যে কি তার সন্ধান জানেনও না, নেনও না। তাই সম্মিলনের মুখপাত্রের, যাদের মনের সর্বাঙ্গে আলস্য ধরেছে সেই শ্রেণীর লোকদের, উপদেশ দিয়েছেন’উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।
এঁরা আমাদের জাগিয়ে তুলতে চান সত্যের জ্ঞানে, আমাদের উঠে চলতে বলেন সত্যের অনুসন্ধানে। কারণ, যে সত্য চোখের সুমুখে রয়েছে সেটিকে দেখাও আমাদের পক্ষে যেমন কর্তব্য, যে সত্য লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বার করাও আমাদের পক্ষে তেমনি কর্তব্য। কোনো জিনিস দেখতে হলে জাগা অর্থাৎ চোখ খোলা দরকার, আর কোনো জিনিস খুজতে হলে ওঠা এবং চলা দরকার। তাই এরা আমাদের উত্তিষ্ঠত জাগ্রত এই মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চান। তবে আমরা এ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে রাজি হব কি না জানি নে; কেননা এ মন্ত্রের সাধনায় আমরা অভ্যস্ত নই।
লোকপ্রবাদ যে, পুরুতে যখন মন্তর পড়ে পাঁঠা তাতে কর্ণপ্লাত করে না। পাঁঠা যে ওসব কথা কানে তোলে না তার কারণ, উৎসর্গের মন্ত্র পড়া হয় ছাগকে বলি দেবার জন্য। কিন্তু এই সাহিত্যযজ্ঞের পুরোহিতেরা যে মন্ত্র পড়েছেন তা বলির মন্ত্র নয়, বোধনের মন্ত্র। সুতরাং তাতে কর্ণপাত করায় আমাদের বিশেষ আপত্তি হওয়া উচিত নয়। আমরা মানি আর না মানি, এরা যে-কথা বলেছেন তা যে মন দিয়ে শোনবার মত কথা, এই বিশ্বাসে আমি সাহিত্যসম্মিলনের অভিভাষণচতুষ্টয়ের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।
২.
পূজ্যপাদ শ্ৰীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তার অভিভাষণের উপসংহারে বলেছেন যে,
বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারতমন্ত্রীর কথা শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন।
এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর মতে ভারতবর্ষই হচ্ছে বিজ্ঞানের জন্মভূমি। কিন্তু পুরাকালে বালক-অবস্থাতেই বিজ্ঞান সমাজের প্রতি অভিমান করে দেশত্যাগী হয়ে ইউরোপে চলে যান। এবং সেখানে তদ্দেশবাসীর যত্নে লালিতপালিত হয়ে এখন যথেষ্টর চাইতেও বেশি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছেন। এমনকি ইউরোপবাসীরা এখন আর তাকে সামলে উঠতে পারছে না। এই কারণেই যিনি স্থূলপথে বিলেত চলে গেছলেন তাঁকে আবার জলপথে দেশে ফিরে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে। ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলে দেশের যে কোনো অকল্যাণ হবে, এ আশঙ্কা ঠাকুরমহাশয় করেন না। বরং তিনি এতে মঙ্গলেরই আশা করেন। কেন? তা তিনি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন নি। তবে তিনি বিজ্ঞানের রূপগুণের যে শাস্ত্ৰসংগত বর্ণনা করেছেন, তার থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে কি কারণে বিজ্ঞানের আবার দেশে ফেরাটা দরকার।
ঠাকুরমহাশয় বলেছেন যে,
বৈদান্তিক আচার্যেরা বলেন সত্য তিন প্রকার : ১ পারমার্থিক সত্য =তত্ত্বজ্ঞান= পরাবিদ্যা, ২ ব্যাবহারিক সত্য = বিজ্ঞান = অপরাবিদ্যা, ৩ প্রাতিভাসিক সত্য ভ্রমজ্ঞান = অবিদ্যা।
বিজ্ঞান বলতে একালে আমরা যা বুঝি সে বিষয়ে বেদান্তের পরিভাষায় সম্যক্ আলোচনা করা কঠিন। কারণ জ্ঞানের এই ত্রিবিধ জাতিভেদ আধুনিক দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। নব্যমতে জ্ঞান এক, শুধু ভ্রমই বহুবিধ। তবুও আমার বিশ্বাস যে, বেদান্তের পরিভাষা অবলম্বন করেও জ্ঞানের রাজ্যে বিজ্ঞানের স্থান কোথায় এবং কতখানি তা দেখানো যেতে পারে। সুতরাং আমি এ প্রবন্ধে উক্ত পরিভাষাই ব্যবহার করব।
ঠাকুরমহাশয় পূর্বোক্ত তিন সত্যের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করেছেন–
বিজ্ঞান ব্যষ্টিজ্ঞান বা শাখাজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান বা মোট জ্ঞান। পারমার্থিক সত্য মোট জ্ঞানের মোট সত্য; ব্যাবহারিক সত্য বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন সত্য।
অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা এক অখণ্ডসত্য লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান; আর যার দ্বারা বহু খণ্ডসত্যের জ্ঞান লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে বিজ্ঞান। এক কথায়, তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষকে জানা; বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতিকে চেনা। বিজ্ঞানের নামে অনেকে ভয় পান এই মনে করে যে তা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী; এবং তত্ত্বজ্ঞান যেহেতু ভারতবর্ষের প্রাণ, অতএব সেটিকে নিরাপদে রাখবার জন্য এদের মতে বিজ্ঞানকে পরিহার করা কর্তব্য। এরূপ কথা অবশ্য বেদবেদান্তে নেই; বরং উপনিষদ্কারেরা বলেছেন যে, অপরাবিদ্যা আয়ত্ত করতে না পারলে পরাবিদ্যায় কারও অধিকার জন্মায় না। উপরোক্ত মতটি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, বিজ্ঞানের চর্চা ত্যাগ করলে বহু সম্বন্ধে আমাদের ভ্রমজ্ঞান হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ বিজ্ঞান হচ্ছে পরীক্ষিত জ্ঞান; বৈজ্ঞানিকেরা। সত্যের টাকা না বাজিয়ে নেন না। বহু খণ্ডসত্যের উপর যদি এক মোটসত্যের প্রতিষ্ঠা না করা যায়, তাহলে বহু খণ্ডমিথ্যার উপর সে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, এরূপ মিছা আশা শুধু পাগলে করতে পারে।
আসল কথা এই যে, দর্শনে আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই দুইটি ভাবকে পৃথক্ করে নিলেও এ বিশ্ব ব্যস্তসমস্ত। তাই সমষ্টির জ্ঞানের ভিতর ব্যষ্টির জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং ব্যষ্টির জ্ঞান সমষ্টির জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। কেননা বস্তুতঃ ও-দুই একসঙ্গে জড়ানো। তত্ত্বজ্ঞানে ও বিজ্ঞানে প্রভেদ এই যে, সমষ্টিজ্ঞান পরাবিদ্যায় একভাবে পাওয়া যায়, আর অপরাবিদ্যায় আর-একভাবে পাওয়া যায়। পরাবিদ্যার সমষ্টিজ্ঞান হচ্ছে মূলতঃ একত্বের জ্ঞান। অপর পক্ষে বহুকে যোগ দিয়ে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তারই জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানানুমোদিত সমষ্টিজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানী এক জেনে সব জানতে চান, আর বৈজ্ঞানিক সবকে একত্র করে জানতে চান। এ দুয়ের ভিতর পার্থক্য আছে কিন্তু বিরোধ নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের চর্চায় পারমার্থিক সত্যের নাশের ভয় নেই, ভয় আছে শুধু মিথ্যা জ্ঞানের উচ্ছেদের। যারা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান তারাই শুধু বিজ্ঞানকে ডরান।
পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রাতিভাসিক সত্য হচ্ছে ভ্ৰমজ্ঞান। এ কথা শুনে লোকের এই ধোঁকা লাগতে পারে যে, কি করে একই জ্ঞান যুগপৎ সত্য ও ভ্রম হতে পারে। প্রাতিভাসিক সত্য যে এক হিসাবে সত্য আর-এক হিসাবে মিথ্যা, এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সম্মিলনের সভাপতিমহাশয় যে-দুটি উদাহরণ দিয়েছেন, তারই সাহায্যে প্রাতিভাসিক সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করব।
সূর্য পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য; আর পৃথিবী যে সূর্যের চার দিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চ্যাপটা, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য; আর পৃথিবী গোলাকার, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চ্যাপটা ও সূর্যের যে উদয়াস্ত হয়, এ দুটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য, অর্থাৎ আমাদের চোখের পক্ষে ও আমাদের চলাফেরার পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য। যতখানি জমি বাংলাদেশে চোখে দেখা যায় তা যে সমতল, এর চাইতে খাঁটি সত্য আর নেই। সুতরাং পৃথিবীর যে খণ্ডদেশ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ, তা চ্যাপটা, গোলাকার নয়। সমগ্র পৃথিবীটি গোলাকার, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীটি প্রত্যক্ষ নয়। আমরা যখন প্রত্যক্ষের সীমা লঙ্ঘন করে অপ্রত্যক্ষের বিষয় প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে জানতে চাই, তখনই আমরা ভ্রমে পড়ি। কারণ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হচ্ছে সমষ্টির জ্ঞান, অসংখ্য খণ্ড খণ্ড প্রত্যক্ষজ্ঞানের যোগাযোগ করে সে জ্ঞান পাওয়া যায়। অসংখ্য চ্যাপটা খণ্ডকে ঠিক দিলে তা গোল হয়ে। ওঠে। এক মুহূর্তে একদেশদর্শিতাই হচ্ছে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ধর্ম, সুতরাং কোনো একটি বিশেষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যকে দাঁড় করানো যায় না।
ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর যে পরিচয় দেয়, সাধারণতঃ মানুষে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট। থাকে, কারণ তাতেই তার কাজ চলে যায়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্ৰহ্মাণ্ডকে একটি প্রকাণ্ড সমষ্টি হিসেবে দেখতে চায়; বিশ্বে একটা নিয়ম আছে এই বিশ্বাসে, সে সেই নিয়মের সন্ধানে ফেরে। বস্তুসকলকে পৃথভাবে না দেখে যুক্তভাবে দেখতে গিয়ে বিজ্ঞান দেখতে পায় যে, প্রতিভাসিক সত্য সমগ্র সত্য নয়। পৃথিবী যে চ্যাপটা ও সূর্য যে পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের হিসেবে। এ দুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং সম্পৰ্করহিত সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে এ দুটি হচ্ছে এক সত্যের দুইটি বিভিন্ন রূপ। পৃথিবী-নামক মৃৎপিণ্ডটি যে কারণে সূর্যের চার পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই কারণেই সেটি তাল পাকিয়ে গেছে। ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ কিংবা চ্যাপটা হলে ওভাবে ঘোরা তার পক্ষে অসাধ্য হত। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই, কারণ এ উভয়ের অধিকার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে চাই বস্তুজগতের সামান্য গুণ, আর প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখতে চাই বস্তুর বিশেষ রূপ। অতএব বিজ্ঞানের চর্চা করলে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান মারা যাবে না অর্থাৎ আমাদের ধর্ম নষ্ট হবে না; এবং আমাদের বাহ্যজ্ঞানও নষ্ট হবে না অর্থাৎ কাব্য-শিল্পও মারা যাবে না। যা তত্ত্বজ্ঞানও নয় বিজ্ঞানও নয় প্রত্যক্ষজ্ঞানও নয়, তাই হচ্ছে যথার্থ মিথ্যা; এবং তারই চর্চা করে আমরা ধর্ম সমাজ কাব্য শিল্প, এক কথায় সমগ্র মানবজীবন, সমূলে ধ্বংস করতে বসেছি।
৩.
বিজ্ঞান শুধু একপ্রকার বিশেষজ্ঞানের নাম নয়; একটি বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, আসলে তারই নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। আমরা বিজ্ঞানকে যতই কেন সাধাসাধি করি নে, সে কখনোই এ দেশে ফিরে আসবে না, যদি-না আমরা তার সাধনা করি। সুতরাং সেই সাধনপদ্ধতিটি আমাদের জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমি দুইএকটি কথা বলতে চাই। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য থেকেই তার উপায়েরও পরিচয় পাওয়া যাবে। তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্ছে এক সত্য’, অথচ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বহুর অস্তিত্ব তত্ত্বজ্ঞানীরাও অস্বীকার করতে পারেন না। তাই বৈদান্তিকেরা বলেন, যা পূর্বে এক ছিল তাই এখন বহুতে পরিণত হয়েছে। সাংখ্যের মতে সৃষ্টি একটি বিকার মাত্র, কেননা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির সুস্থ অবস্থা। সৃষ্টিকে বিকার হিসেবে দেখা আশ্চর্য নয়, কেননা আপাতসুলভ জ্ঞানে এ বিশ্ব একটি ভাঙাচোরা, ছাড়ানো ও ছড়ানো ব্যাপার। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই অসংখ্য পৃথক পৃথক্ বস্তুর পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা, জড়জগতের ভগ্নাংশগুলিকে যোগ দিয়ে একটি মন দিয়ে ধরবার-ছোঁবার মত সমষ্টি গড়ে তোেল। এই ভগ্নাংশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যোগ করতে হলে আঁকজোখ চাই। সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে চার করার নামই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ আর-যে-দেশেই হোক, বিজ্ঞানের রাজ্যে হয় না। বিজ্ঞানের কারবার শুধু বস্তুর সংখ্যা নিয়ে নয়, পরিমাণ নিয়েও। সুতরাং বিজ্ঞানে মাপজোখও করা চাই। বিনা মাপে বিনা আঁকে যে সত্য পাওয়া যায়, তা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। বিজ্ঞানের যা-কিছু মর্যাদা, গৌরব ও মূল্য, তা সবই এই পদ্ধতির দরুন। আমাদের কাছে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ কিছু মূল্য নেই, যদি আমরা কি উপায়ে সেটি পাওয়া গেছে তা না জানি। পৃথিবী কমলালেবুর মত, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু কি মাপজোখের কি যুক্তির সাহায্যে এই সত্য নির্ণীত হয়েছে, সেটি না জানলে ও-সত্য আমাদের মনের হাতে কমলালেবু নয়, ছেলের হাতে মোয়া; অর্থাৎ তা আমাদের এতই কম করায়ত্ত যে, যে-খুশি-সেই কেড়ে নিতে পারে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসকলের ক্রমান্বয় ভুল বেরচ্ছে, আবার তা সংশোধন করা হচ্ছে। কিন্তু সে ভুলের আবিষ্কার ও সংশোধন ঐ একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সাধিত হচ্ছে।
ঐতিহাসিক শাখার নেতা শ্ৰীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করবার পদ্ধতিটি যে কি, তারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন; কারণ ইতিহাস ঠিক বিজ্ঞান না হলেও একটি উপবিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য। এ ক্ষেত্রে মৈত্রেয়মহাশয়ের মতে ঐতিহাসিকদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অনুসন্ধান করে অতীতের দলিল সংগ্রহ করা। সে দলিল নানা দেশে নানা স্থানে ছড়ানো আছে। সুতরাং সেইসব হারামণির অন্বেষণের জন্য ঐতিহাসিকদের দেশদেশান্তরে ঘুরতে হবে। শুধু তাই নয়। ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল সময়ে মাটির উপর পড়ে-পাওয়া যায় না। ও হচ্ছে বেশির ভাগ কষ্ট করে উদ্ধার করবার জিনিস। কারণ অতীত প্রত্যক্ষ নয়, বর্তমানে তা ঢাকা পড়ে থাকে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করবার অর্থ হচ্ছে অ-দৃষ্টকে দৃষ্ট করা, তার জন্য চাই পুরুষকার। তাই মৈত্রেয়মহাশয় কেবলমাত্র ভক্তিভরে অতীতের নাম কীর্তন না করে তার সাক্ষাৎকার লাভ করবার পরামর্শ আমাদের দিয়েছেন। তার পরামর্শমত কাজ করতে হলে আমাদের করতাল ভেঙে কোদাল গড়াতে হবে। ভূগর্ভে ও কালগর্ভে যেসকল ঐতিহাসিক রত্ন নিহিত আছে আগে তা খুঁড়ে বার করতে হবে, পরে তার কাটাইছাটাই করে সাহিত্যসমাজে প্রচলন করতে হবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, আগে আসে খনিকার, তার পরে মণিকার। মৈত্রেয়মহাশয় তাই ঐতিহাসিকদের কলম ছাড়িয়ে খন্তা ধরাতে চান। তার বিশ্বাস যে, ঐতিহাসিকদের হাতের খন্তা নিয়ত ব্যবহারে ক্ষয়ে গিয়ে ক্রমশঃ কলমের আকার ধারণ করবে, এবং সেই কলমে ইতিহাস লিখতে হবে। ইতিহাসের আবিষ্কর্তা ও রচয়িতার মধ্যে যে অধিকারভেদ আছে, মৈত্রেয়মহাশয় বোধ হয় সেটি মানেন না। অথচ এ কথা সত্য যে একজনের পক্ষে কলম ছেড়ে খন্তা ধরা যত কঠিন, আর-একজনের পক্ষে খন্তা ছেড়ে কলম ধরা তার চাইতে কিছু কম কঠিন নয়।
সে যাই হোক, মৈত্রেয়মহাশয় আমাদের আর-একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সে হচ্ছে এই যে, ত্যাগ স্বীকার না করতে পারলে কোনোরূপ সাধনা করা যায় না। কেননা, ত্যাগের অভ্যাস থেকেই সংযমের শিক্ষা লাভ করা যায়। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সাধনা করতে হলে আমাদের অসংখ্য মানসিক-আলস্যপ্রসূত বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। আমাদের পুরাণের মায়া, কিংবদন্তীর মোহ কাটাতে হবে।
শুধু রূপকথা নয়, সেই সঙ্গে কথার মোহও আমাদের ত্যাগ করতে হবে; অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাস রচনা করতে হলে সে রচনায় ‘শব্দের লালিত্য, বর্ণনার মাধুর্য, ভাষার চাতুর্য পরিহার করতে হবে। এক কথায় শ্রীহর্ষচরিত আর কাদম্বরীর ভাষায় লেখা চলবে না। এ কথা অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু কি কারণে অক্ষয়বাবু অপরকে যে-উপদেশ দিয়েছেন নিজে সে-উপদেশ অনুসরণ করেন নি তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। কারণ তার অভিভাষণের ভাষা যে ‘অক্ষর-ডম্বর’, এ কথা টাউনহলে সশরীরে উপস্থিত থাকলে স্বয়ং বাণভট্টও স্বীকার করতেন। সম্ভবতঃ অক্ষয়বাবুর মতে ইতিহাসের আখ্যান হচ্ছে বিজ্ঞান, আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাখ্যান হচ্ছে কাব্য।
৪.
যে লোভ অক্ষয়বাবু সংবরণ করতে পারেন নি, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। শাস্ত্রীমহাশয় আগাগোড়া অশাস্ত্রীয় ভাষা ব্যবহার করায় তার অভিভাষণ এতই জলের মত সহজ হয়েছে যে, তা এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করা যায়। এ শ্রেণীর লেখা যে বহতা নদীর জলের
মতই স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। জলের মত ভাষার বিশেষ গুণ এই যে, তা জ্ঞানপিপাসুদের তৃষ্ণা সহজেই নিবারণ করে। বর্ণ-গন্ধ চাই শুধু কাব্যের ভাষায়, কেননা তা হয় অমৃত নয় সুরা।
আমি বহুকাল হতে এই কথা বলে আসছি যে, বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই সহজ কথাটি অনেকের কাছে এতই দুর্বোধ ঠেকে যে, তারা এরূপ আজগুবি কথা শুনে বিরক্ত হন। এদের মতে বাংলা হচ্ছে আমাদের আটপৌরে ভাষা, তাতে সাহিত্যের ভদ্রতা রক্ষা হয় না। সুতরাং সাহিত্যের জন্য সাধুভাষা নামক একটি পোশাকি ভাষা তৈরি করা চাই। পোশাক যখন চাইই, তখন তা যত ভারী আর যত জমকালো হয় ততই ভালো। তাই সাহিত্যিকরা সংস্কৃত ভাষার চোরা-জরিতে কিংখাব বুনতে এতই ব্যগ্র ও এতই ব্যস্ত যে, সে জরি সাচ্চা কি বুটা, তা দিয়ে তারা কিংখাব দূরে থাক্ দোসুতিও বুনতে পারেন কি না, পারলেও সে বুনানিতে ঐ জরি খাপ খায় কি না, এসব বিচার করবার তাঁদের সময় নেই। সুতরাং বাংলা লিখতে বললে তারা মনে করেন যে, আমরা তাদের কাব্যের বস্ত্রহরণ করতে উদ্যত হয়েছি। কিন্তু আমরা যে ওরূপ কোনো গহিত আচরণ করতে চাই নে, তার প্রমাণ, ভাষা ভাবের লজ্জা নিবারণ করবার জিনিস নয়। ভাষা বস্ত্র নয়, ভাবের দেহ; আলংকারিকদের ভাষায় যাকে বলে ‘কাব্যশরীর। বাঙালির ভাষা বাঙালি চৈতন্যের অধিষ্ঠান। বাঙালির আত্মাকে সংস্কৃত ভাষার দেহে কেউ প্রবেশ করিয়ে দিলে ব্যাড়ীর আত্মা নন্দ-ভূপতির দেহে প্রবেশ করে যেরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল সেইরূপ হবারই সম্ভাবনা। দরিদ্র ব্রাহ্মণের আত্মা রাজার দেহে প্রবেশ করায় তার। যে কি পর্যন্ত দুর্গতি হয়েছিল তার বিস্তৃত ইতিহাস কথাসরিৎসাগরে দেখতে পাবেন। বাঙালির স্কুলে-পড়ানো আত্মা কেন যে নিজের দেহপিঞ্জর হতে নিষ্ক্রমণ করে পরের পঞ্জরে প্রবেশলাভ করবার জন্য ছটফট করছে, তার কারণ শাস্ত্রীমহাশয়ই নির্দেশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন
আমার বিশ্বাস, বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন কোনো ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন। আমরাও তেমনি বাঙালি জাতির অজ্ঞান অবতার, সম্ভবতঃ গুরু-পুরোহিতের শাপে। মুক্তির জন্য আমাদের এই শাপমুক্ত হতে হবে, অর্থাৎ জাতিস্মর হতে হবে। কেননা, সত্যলাভের জন্য যেমন বাহ্যজ্ঞান চাই, তেমনি আত্মজ্ঞানও চাই। এই জাতিস্মরতা লাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইতিহাস। একমাত্র ইতিহাসই জাতির পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জাতীয় পূর্বজন্মের জ্ঞান হারিয়েই আমরা নিজের ভাষার মনের ও চরিত্রের, জ্ঞান হারিয়েছি।
শাস্ত্রীমহাশয়ের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, এক ‘আর্য’ শব্দের উপর জীবন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বাঙালির ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হবে, কেননা আমরা মোক্ষমুলারের আবিষ্কৃত খাঁটি আর্য নই। আমরা একটি মিশ্রজাতি। প্রথমতঃ দ্রবিড় ও মংগলের মিশ্রণে বাঙালি জাতি গঠিত হয়। তার পর সেই জাতির দেহে মনে ও সমাজে কতক পরিমাণ আর্যত্ব আরোপিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আমরা একেবারে আর্যমিশ্র হয়ে উঠি নি। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আর্যসভ্যতা আবর্তে আবর্তে বাংলায় এসে পৌঁছেছে। তিনি বলেন
এইসকল আবর্ত ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাংলায় আসিয়া উপনীত হয়, তখন দেখা যায় আর্যের মাত্রা বড়ই কম, দেশির মাত্রা অনেক বেশি এ সত্য আমি নিরাপত্তিতে স্বীকার করি, যদিচ সম্ভবতঃ আমি এই ক্রমাগত আর্য-আবর্তের একটি ক্ষুদ্র বুদবুদ, কেননা আমি ব্রাহ্মণ।
বাংলা ভাষা আর্য ভাষা নয়, উক্ত ভাষার একটি স্বতন্ত্র শাখা–এক। কথায় একটি নবশাখ ভাষা। বাঙালি জাতিও আর্য জাতি নয়, একটি নবশাখ জাতি। আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান চেষ্টা হয়েছে আমাদের মন ও ভাষার মধ্যে থেকে তার দেশি খাদটুকু বাদ দিয়ে তার আর্য সোনাটুকু বার করে নেওয়া। প্রথমতঃ ওরূপ খাদ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, দ্বিতীয়তঃ সম্ভব হলেও বড় বেশি যে সোনা মিলবে তাও নয়। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, দেশি অংশটুকু বাদ দেবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন। ও তত খাদ নয়, ওই তো হচ্ছে। বাঙালি জাতির মূলধাতু। এবং সে ধাতু যে অবজ্ঞা কিংবা উপেক্ষা করবার জিনিস নয়, তা যিনিই বাঙালির প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান রাখেন তিনিই মানেন। কঁঠাল আম নয় বলে দুঃখ করবারও কারণ নেই, এবং কাঁঠালের ডালে আমের কলম বাবার চেষ্টা করবারও দরকার নেই। আমরা এই বাংলার গায়ে হয় ইংরেজি নয় সংস্কৃতের কলম বসিয়ে সাহিত্যে ও জীবনে শুধু কঁঠালের আমসত্ত্ব তৈরি করবার বৃথা চেষ্টা করছি।
শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, বাঙালি জাতির প্রাচীন সিদ্ধাচার্যের সব সহজিয়া মতের প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন। আমরা আত্মজ্ঞানশূন্য বলে যা আমাদের কাছে সহজ তাই বর্জন করি; আমরা সাধুভাষায় সাহিত্য লিখি, আর জীবনে হয় সাহেবিয়ানা নয় আর্যামি করি। জাতীয় আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারলে আমরা আবার সহজ অর্থাৎ natural হতে পারব। মনের এই সহজসাধন অতি কঠিন ব্যাপার, কেননা আমাদের সকল শিক্ষাদীক্ষা হচ্ছে কৃত্রিমতার সহায় ও সম্পদ।
৫.
সাহিত্যশাখার সভাপতি শ্ৰীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ও আমাদের বলেছেন যে–
আলস্যের প্রশ্রয় দিলে হইবে না। নিদ্রিত সমাজকে জাগাইতে হইবে। শয্যাশয়ান সমাজের সুখসুপ্তি ভাঙাইতে হইবে।
এ যে শুধু কথার কথা নয়, তার প্রমাণ, কি করে সাহিত্যের সাহায্যে সমাজকে জাগিয়ে তুলতে পারা যায় তার পন্থা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তার মোট কথা এই যে, দর্শনবিজ্ঞানের চর্চা না করলে সাহিত্য শক্তিহীন ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। তর্করত্নমহাশয়ের মতে ‘সাহিত্য’ শব্দের অর্থ সাহচর্য। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, কিসের সাহচর্য? তার উত্তর, সকল প্রকার জ্ঞানের সাহচর্য। কারণ অতিপ্রবৃদ্ধ অজ্ঞতার গর্ভে যে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে তা সুকুমার-সাহিত্য নয়, তা শুধু কুমার-সাহিত্য অর্থাৎ ছেলেমানুষি লেখা। তিনি দেখিয়েছেন যে, কালিদাস প্রভৃতি বড় বড় সংস্কৃত কবিরা সে যুগের সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রমাণ, শকুন্তলা অভিজ্ঞান, অবিজ্ঞান নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা যুক্ত শাস্ত্রের জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা সংস্কৃত কাব্য আধো বুঝি, সংস্কৃত দর্শন ভুল বুঝি, পুরাণকে ইতিহাস বলে গণ্য করি, আর ধর্মশাস্ত্রকে বেদবাক্য বলে মান্য করি।
সে যাই হোক, পাণ্ডিত্য কস্মিকালেও সাহিত্যের বিরোধী নয়। তার প্রমাণ, কালিদাস দান্তে মিল্টন গ্যেটে প্রভৃতি। তবে, পণ্ডিত অর্থে যদি বিদ্যার চিনির বলদ ববাঝায় তাহলে সে স্বতন্ত্র কথা। জ্ঞানই হচ্ছে কাব্যের ভিত্তি, কারণ সত্যের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। তর্করত্নমহাশয়ের বক্তব্য এই যে, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে ‘সিথেটিক কালচার তাই হচ্ছে সাহিত্যের পরম সহায়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। ইউরোপের দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব রাজনীতির সঙ্গে কতকটা পরিচয় না থাকলে কোনো বড় ইংরেজ কবি কিংবা নভেলিস্টের লেখা সম্পূর্ণ বোঝাও যায় না, তার রসও আস্বাদন করা যায় না। সাহিত্য হচ্ছে প্রবুদ্ধ চৈতন্যের বিকাশ; এবং চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলতে হলে তার উপর আর-পাঁচজনের মনের আর-পাঁচরকমের জ্ঞানের ধাক্কা চাই। যার মন সত্যের স্পর্শে সাড়া দেয় না, সে সত্য আধ্যাত্মিকই হোক আর আধিভৌতিকই হোক, তিনি কবি নন। সুতরাং দর্শন-বিজ্ঞানকে অস্পৃশ্য করে তোলায় কাব্যের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। এই কারণেই তর্করত্নমহাশয় আমাদের দেশি-বিলাতি সকল প্রকার দর্শন-বিজ্ঞান অনুবাদ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তার মতে আলস্যপ্রিয় বাঙালি-মনের পক্ষে বিজ্ঞানচর্চারূপ মানসিক ব্যায়াম হচ্ছে অত্যাবশ্যক। আমাদের অলস মনের আরামজনক বিশ্বাস-সকল বিজ্ঞানের অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ না হলে সত্যের খাঁটি সোনাতে তা পরিণত হবে না; আর যা খাঁটি সোনা নয়, তার অলংকার ধারণ করলে কাব্যের দেহও কলঙ্কিত হয়।
৬.
এবারকার সাহিত্যসম্মিলনের ফলে যদি বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের মিলন হয়, তা হলে বঙ্গসাহিত্যের দেহ ও কান্তি দুইই পুষ্ট হবে। সে মিলন যে কবে হবে তা জানি নে। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আমাদের ভাবের ও ভাষার বিচ্ছেদটি যে বহু লোকের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে, এইটি হচ্ছে মহা আশার কথা। মিথ্যার প্রতি আগে বিরাগ না জন্মালে কেউ সত্যের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করেন না। কারণ সে পথে কষ্ট আছে। বিজ্ঞানের মন্দিরে, অর্থাৎ সত্যের মানমন্দিরে পৌঁছতে হলে আগাগোড়া সিঁড়ি ভাঙা চাই।
আমি বৈজ্ঞানিক নই, কাজেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আমার মনের প্রধান সম্বল। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্যেরা কেউ দুটি ভালো কথা বলেন নি। তাই আমি তার সপক্ষে কিছু বলতে বাধ্য হচ্ছি।
বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতিরিক্ত হলেও ঐ মূলজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাহ্যবস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করতে হলে ইন্দ্রিয়েরও একটা শিক্ষা চাই। অনেকে চোখ থাকতেও কানা, কান থাকতেও কালা, অথচ মুখ না থাকলেও মূক নন। এই শ্রেণীর লোকের বাচালতার গুণেই আজ বাংলা সাহিত্যের কোনো মর্যাদা নেই। কাব্যকে আবার সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করতে হলে ইন্দ্রিয়কে আবার সজাগ করে তোলা চাই। চোখও বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের ঠকাতে পারে, যদি সে চোখ ঘুমে ঢলে। অপর পক্ষে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকলেও যা স্পষ্ট তাও আমাদের কাছে ঝাপসা হয়ে যায়। চোখে আর মনে এক না করতে পারলে কোনো পদার্থ লক্ষ্য করা যায় না। ইন্দ্রিয় ও মনের এই একীকরণ সাধনা বিনা সিদ্ধ হয় না। যাঁরা কাব্য রচনা করবেন, তাদের পক্ষে বাহিরের ভিতরের সকল সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। কারণ কাব্যে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর কোনো সত্যের স্থান নেই। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর অবিশ্বাস এবং তার। প্রতি অমনোযোগ হচ্ছে কাব্যে সকল সর্বনাশের মূল। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবশ্য নিজের সীমা লঙ্ঘন করলে মিথ্যা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। বিজ্ঞানও তেমনি নিজের সীমা লঙ্ঘন করলে মিথ্যা তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়। তার কারণ, বিজ্ঞান কোনো পদার্থকে এক হিসেবে দেখতে পারে না। বিজ্ঞান যে সমষ্টি খোজে সে হচ্ছে সংখ্যার সমষ্টি। বিজ্ঞান চারকে এক করতে পারে না। বিজ্ঞান চারকে পাওয়ামাত্র হয় তাকে দুই দিয়ে ভাগ করে, নয় তার থেকে দুই বিয়োগ করে; পরে আবার হয় দুই দ্বিগুণে, নয় দুয়ে-দুয়ে চার করে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যার উপর হস্তক্ষেপ করে তাকে আগে ভাঙে, পরে আবার জোড়াতাড়া দিয়ে গড়ে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, বিজ্ঞানের হাতে জল হয় বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, নয় বরফ হয়ে জমে থাকে; আর না হয় তো এক ভাগ অক্সিজেন আর দু ভাগ হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তার পর বিজ্ঞান আবার সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে সেই বরফকে তাতিয়ে জল করে দেয়, এবং অক্সিজেনে-হাইড্রোজেনে পুনর্মিলন করে দেয়।
কিন্তু আমরা এক নজরে যা দেখতে পাই, তাই হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এ জ্ঞানও একের জ্ঞান, অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানের সবর্ণ।
ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
এ কথা তাঁরই কাছে সত্য, যাঁর কাছে এটি প্রত্যক্ষ সত্য। কেননা, কোনোরূপ আঁকের সাহায্যে কিংবা মাপের সাহায্যে ও-সত্য পাওয়া যায় না। একত্বের জ্ঞান কেবলমাত্র অনুভূতিসাপেক্ষ।
আমি পূর্বে বলেছি, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামে মনঃসংযোগ করা চাই; সেই মনঃসংযোগের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা চাই, এবং সেই ইচ্ছার মূলে আন্তরিক অনুরাগ চাই; এবং এ অনুরাগ অহৈতুকী প্রীতি হওয়া চাই। কোনোরূপ স্বার্থসাধনের জন্য যে সত্য আমরা খুজি, তা কখনো সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। যে প্রীতির মূলে আমার সহজ প্রবৃত্তি নেই, তা কখনো অহৈতুকী হতে পারে। সুতরাং সত্য যে সুন্দর, এই জ্ঞানলাভের উপায় হচ্ছে সহজসাধন, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা কঠিন সাধন। কারণ আত্মার উপর বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।
সে যাই হোক, বিজ্ঞানের অবিরোধে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চর্চা করা যায়, এ বিশ্বাস হারালে আমরা কাব্য-শিল্প সৃষ্টি করতে পারি নে। বিজ্ঞান হচ্ছে পূর্বসৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান। নূতন সৃষ্টির হিসাব বিজ্ঞানের পাকা খাতায় পাওয়া যায় না। সৃষ্টির মূলে যে চিররহস্য আছে, তা কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এই কারণে দেশের লোককে বিজ্ঞানের চর্চা করবার পরামর্শ দেওয়াটা সৎপরামর্শ, কেননা যা স্পষ্ট তাতে সর্বসাধারণের সমান অধিকার আছে। অপর পক্ষে কাব্যে শিল্পে অধিকারীভেদ আছে। সত্যের মূর্তিদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না।
১৩২১ জ্যৈষ্ঠ
সাহিত্যে খেলা
জগৎবিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর রোড্যাঁ, যিনি নিতান্ত জড় প্রস্তরের দেহ থেকে অসংখ্য জীবিতপ্রায় দেবদানব কেটে বার করেছেন, তিনিও, শুনতে পাই, যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে আঙুলের টিপে মাটির পুতুল তয়ের করে থাকেন। এই পুতুল-গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা। শুধু রোড্যাঁ কেন, পৃথিবীর শিল্পীমাত্রেই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। যিনি গড়তে জানেন, তিনি শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড়-বড় শিল্পীদের তফাত এইটুকু যে, তাঁদের হাতে এক করতে আর হয় না। সম্ভবত এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুশি-তাই করবার যে অধিকার আছে, ইতর শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হতে দেবতারা মধ্যেমধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে কেউ আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্তবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়। অথচ একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, যখন এ জগতে দশটা দিক আছে, তখন এইসব-দিকেই গতায়াত করবার প্রবত্তিটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মন উচুতেও উঠতে চায়, নীচুতেও নামতে চায়; বরং সত্যকথা বলতে গেলে, সাধারণ লোকের মন স্বভাবতই যেখানে আছে তারই চারপাশে ঘুরে বেড়াতে চায় উড়তেও চায় না, ডুবতেও চায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে সাধারণ লোককে, কি ধর্ম, কি নীতি, কি কাব্য সকল রাজ্যেই অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাকতেই পরামর্শ দেয়। একটু উচুতে না চড়লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন-মন আকর্ষণ করতে পারি নে। বেদিতে না বসলে আমাদের উপদেশ কেউ মানে না, রঙ্গমঞ্চে না চড়লে আমাদের অভিনয় কেউ দেখে না, আর কাঠমঞ্চে না দাঁড়ালে আমাদের বক্তৃতা কেউ শোনে না। সুতরাং জনসাধারণের চোখের সম্মখে থাকবার লোভে আমরাও অগত্যা চব্বিশঘণ্টা টঙে চড়ে থাকতে চাই, কিন্তু পারি নে। অনেকের পক্ষে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত উচ্চস্থানে ওঠবার চেষ্টাটাই মহাপতনের কারণ হয়। এসব কথা বলবার অর্থ এই যে, কষ্টকর হলেও আমাদের পক্ষে অবশ্য মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই কর্তব্য; কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে ছোটখাট গলিঘজিতে খেলাচ্ছলে প্রবেশ করবার যে অধিকার তাঁদের আছে, সে অধিকারে আমরা কেন বঞ্চিত হব। গান করতে গেলেই যে সুর তারায় চড়িয়ে রাখতে হবে, কবিতা লিখতে হলেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রখর ভাব প্রকাশ করতে হবে, এমন-কোনো নিয়ম থাকা উচিত নয়। শিল্পরাজ্যে খেলা করবার প্রবৃত্তির ন্যায় অধিকারও বড়-ছোট সকলেরই সমান আছে। এমনকি, একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে, এ পৃথিবীতে একমাত্র খেলার ময়দানে ব্রাহ্মণ-শদ্রের প্রভেদ নাই। রাজার ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের ছেলেরও খেলায় যোগ দেবার অধিকার আছে। আমরা যদি একবার সাহস করে কেবলমাত্র খেলা করবার জন্য সাহিত্যজগতে প্রবেশ করি, তাহলে নির্বিবাদে সে জগতের রাজারাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনোরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সেক্ষেত্রে উপস্থিত হলেই নিম্ন শ্রেণীতে পড়ে যেতে হবে।
২.
লেখকেরাও অবশ্য দলের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন, বাহবা না পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন; কেননা, তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ সামাজিক জীব, বাদবাকি সকলে কেবলমাত্র পারিবারিক। বিশ্বমানবের মনের সঙ্গে নিত্যনূতন সম্বন্ধ পাতানোই হচ্ছে কবি-মনের নিত্যনৈমিত্তিক কম। এমনকি, কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতিকবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তিস্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই মর্মকথা হাজার লোকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চবাচ্য করলে যে জনসাধারণের নয়নমন আকর্ষণ করা যায় না, এমন-কোনো কথা নেই। সাহিত্যজগতে যাঁদের খেলা করবার প্রবত্তি আছে, সাহস আছে ও ক্ষমতা আছে— মানুষের নয়ন-মন আকর্ষণ করবার সুযোগ বিশেষ করে তাঁদের কপালেই ঘটে। মানুষে যে খেলা দেখতে ভালোবাসে, তার পরিচয় তো আমরা এই জড় সমাজেও নিত্যই পাই। টাউনহলে বক্তৃতা শুনতেই বা ক’জন যায় আর গড়ের মাঠে ফটবল-খেলা দেখতেই বা ক’জন যায়। অথচ একথাও সত্য যে, টাউন-হলের বক্তৃতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ— ভারত-উদ্ধার; আর গড়ের মাঠের খেলোয়াড়দের ছটোছটি দৌড়াদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীন। আসল কথা এই যে, মানুষের দেহমনের সকলপ্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ; কেননা, তা উদ্দেশ্যহীন। মানুষে যখন খেলা করে, তখন সে এক আনন্দ ব্যতীত অপরকোনো ফলের আকাক্ষা রাখে না। যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই কিন্তু উপরি-পাওনার আশা আছে, তার নাম খেলা নয়, জয়াখেলা। ও-ব্যাপার সাহিত্যে চলে না; কেননা, ধমত জয়াখেলা লক্ষ্মীপজার অগ, সরস্বতীপূজার নয়। এবং যেহেতু খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয়, সে কারণ তা কারও নিজস্ব হতে পারে না। এ আনন্দে সকলেরই অধিকার সমান।
সুতরাং সাহিত্যে খেলা করবার অধিকার যে আমাদের আছে, শুধু তাই নয়— স্বার্থ এবং পরাধএ দুয়ের যুগপৎ সাধনের জন্য মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্বপ্রধান কর্তব্য। যে লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে ব্রতী হন, যিনি কোনোরূপ কার্য-উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন, তিনি গীতের মর্মও বোঝেন না, গীতার ধর্মও বোঝেন না; কেননা, খেলা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। স্বয়ং ভগবান বলেছেন, যদিচ তাঁর কোনোই অভাব নেই তবুও তিনি এই বিশ্ব সজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরুপ, সে সজনের মূলে কোনো অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার ক্ষতি এবং তার ফল আনন্দ। এককথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র, এবং সে লীলা বিলীলার অন্তর্ভূত; কেননা, জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ।
৩.
সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝমঝমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক— এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। কারণ পাঠকসমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে; সে প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জমানিরই হোক, দু দিন ধরে তা কারও মনোরঞ্জন করতে পারে না। আমি জানি যে, পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শই বেদনা বোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই; কেননা, কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা। সে যাই হোক, পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন, তার জাজল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরে অপূর্ব মিলন সংঘটিত হত; কেননা, knowledge এবং art উভয়ই তাঁর সম্পর্ক করায়ত্ত ছিল। ‘বিদ্যাসুন্দর’ খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা— সবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলংকৃত; তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্তত জহরির কাছে। অপরপক্ষে, এ যুগে পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ; সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে আমাদের অতি শস্তা খেলনা গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না। এবং শস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শদ পাঠকের মনোরঞ্জন করা সংগত। অতএব সাহিত্যে আর যাই কর না কেন, পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা কোরো না।
৪.
তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া?–অবশ্য নয়। কেননা, কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যরচনা যে আত্মার লীলা, একথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্মকর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমত, শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু, যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে; কেননা, শাস্ত্রমতে সে রস অমত। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো; সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো। কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, একথা সকলেই জানেন। তৃতীয়ত, অপরের মনের অভাব পর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দদান করা শিক্ষাদান করা নয়–একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি আদিতে মনিঋষিদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন, জনগণের জন্য নয়। একথা বলা বাহুল্য যে, বড়-বড় মনিঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ— তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্বস্ব, এমনকি কৌপীন পর্যন্ত, পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্য হিসাবে যে অমর এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে-পঠনে আনন্দ উপভোগ করে, তার একমাত্র কারণ আনন্দের ধর্মই এই যে তা সংক্রামক। অপরপক্ষে, লাখে একজনও যে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের ছায়া মাড়ান না, তার কারণ সে বহু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জন্যে নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুলমাস্টারির ভার নেয় নি। এতে দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাস্টারেরা একালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।
কাব্যরসনামক অমতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী এ যুগের স্কুল এবং তার মাস্টার। কাব্য পড়বার ও বোঝবার জিনিস; কিন্তু স্কুলমাস্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুলমাস্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে যাক, চারচক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমরা কাব্যের রূপে দেখতে পাই নে, শুধু তার গুণ শনি। টীকা-ভাষ্যের প্রসাদে আমরা কাব্য সম্বন্ধে সকল নিগুঢ়তত্ত্ব জানি; কিন্তু সে যে কি বস্তু, তা চিনি নে। আমাদের শিক্ষকদের প্রসাদে আমাদের এ জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, পাথরে কয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র; অপরপক্ষে, হীরক ও কাঁচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, অপরটির মানুষের হাতে; এবং এ উভয়ের ভিতর এক দা-কুমড়ার সম্বন্ধ ব্যতীত অপর-কোনো সম্বন্ধ নেই। অথচ এত জ্ঞান সত্ত্বেও আমরা সাহিত্যে কাঁচকে হীরা এবং হীরাকে কাঁচ বলে নিত্য ভুল করি; এবং হীরা ও কয়লাকে একশ্রেণীভুক্ত করতে তিলমাত্র দ্বিধা করি নে; কেননা, ওরূপ করা যে সংগত, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের মুখস্থ আছে। সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তার পরে তার শবচ্ছেদ করা এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এইসব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গরুর হাতের বেতও নয়। বিচারের সাহায্যে এই মাত্রই প্রমাণ করা যায়। তবে বস্তু যে কি, তার জ্ঞান অনুভূতিসাপেক্ষ, তর্কসাপেক্ষ নয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে; এ কথার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয়, তাহলে কোনো সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পষ্টতর করা আমার অসাধ্য।
এইসব কথা শুনে আমার জনৈক শিক্ষাভক্ত বন্ধ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়। একথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, সরস্বতীকে কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্ৰীতে পরিণত করবার জন্য যতদূর শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার, আমি আজও ততদুর হতে পারি নি।
শ্রাবণ ১৩২২
হর্ষচরিত
বাণভট্ট বলেছেন—
সাধুনামুপকর্তং লক্ষ্মীং দ্রষ্টুং বিহায়সা গন্তুম্।
ন কুতূহলি কস্য মনশ্চরিতং চ মহাত্মনাং শ্রোতুম্।
লক্ষ্মীকে দেখবার লোভ আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু সাধু ব্যক্তির উপকার করতে অথবা মহাপুরুষের জীবনচরিত শুনতে আমাদের সকলেরই সমান কৌতূহল আছে কি না বলা শক্ত। আর আকাশে উড়বার শখ আমাদের ক’জনের আছে জানি নে। যদিচ এই গরুড়যন্ত্রে, ভাষান্তরে এরোপ্লেনের আমলে, নিজের পকেট কিঞ্চিং হালকা করলেই ও-উড়োগাড়িতে অনায়াসে চড়ে হাওয়া খাওয়া যায়। বাণভট্টের যুগে, অর্থাৎ আজ থেকে তেরো শ বৎসর পূর্বে, ভারতবর্ষের জনগণের ‘বিহায়সা গন্তুম্’এর যে প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল, এ কথা একেবারেই অবিশ্বাস্য।
তবে বাণভট্টের সকল কথারই যখন দ্ব্যর্থ আছে, তখন খুব সম্ভবতঃ তিনি বলেছেন যে, মহাত্মার জীবনচরিত শোনা হচ্ছে মনোজগতে মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠা— ইংরেজিতে যাকে বলে higher plane আমাদের সাংসারিক মনকে সেই ঊর্ধ্বলোকে তোলা।
অপর মহাপুরুষদের বিষয় যাই হোক, যথা বুদ্ধদেব অথবা যীশুখৃস্ট–বাণভট্ট যে-মহাপুরুষের জীবনচরিত বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ মহারাজ হর্ষবর্ধনের, সে-মহাপুরুষের আখ্যান শোনবার জন্য এ যুগে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর কৌতূহল আছে। কারণ, তিনি নিজ বাহুবলে দিগ্বিজয় করে উত্তরাপথের সম্রাট হয়েছিলেন। এ যুগে আমাদের সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্দুমাত্র নেই; সুতরাং পুরাকালে যে-যে স্বদেশি রাজা ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবতী হয়েছিলেন, তাদের জীবনচরিত আমরা সকলেই মন দিয়ে শুনতে চাই। পৃথিবীর দাবাখেলায় এখন আমরা বড়ের জাত; তাই আমরা যদি এ খেলায় কাউকে বাজিমাত করতে চাই, সে হচ্ছে বড়ের চালে চালমাত। সুতরাং আমাদের জাতের মধ্যেও যে অতীতে রাজা ও মন্ত্রী ছিলেন, এ আমাদের কাছে মহা সুসমাচার। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ শ্রেণীর এক-রাটের দর্শন বড় বেশি মেলে না। প্রথম ছিলেন অশোক, তার পর সমুদ্রগুপ্ত, আর শেষ হচ্ছেন হর্ষবর্ধন–আর যদি কেউ থাকেন তা তিনি ইতিহাসের বহির্ভূত।
২.
দুঃখের বিষয়, এ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কৌতূহল চরিতার্থ করা আমাদের, অর্থাৎ বর্তমান যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, পক্ষে একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।
হর্ষ সম্বন্ধে দু জন লোক দু ভাষায় দুখানি বই লিখেছেন, এবং সেই দুখানি বইয়ের উপরই আমাদের হর্ষচরিত খাড়া করতে হবে। একটি লেখক হচ্ছেন হিউয়েন সাং ওরফে ইউয়ান চোয়াং নামক চৈনিক পরিব্রাজক; এবং দ্বিতীয় লেখক হচ্ছেন বাণভট্ট। চীনে লেখক অবশ্য চীনে ভাষাতেই লিখেছেন, আর বলা বাহুল্য, সে ভাষায় বর্ণপরিচয় আমাদের কারও হয় নি। ফলে তার গ্রন্থ থেকে হর্ষের ইতিহাস উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।
তার পর বাণভট্টের হর্ষচরিতের অর্থ গ্রহণ করা অসাধ্য না হক, দুঃসাধ্য; শুধু আমাদের পক্ষে নয়, পণ্ডিতমহাশয়দের পক্ষেও।
বাংলাদেশে ১৯৩৯ সংবতে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে মূল হর্ষচরিত প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন–
বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূবে অবগত ছিলাম না।
এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, অপর কোনো পণ্ডিতই অবগত ছিলেন না। আর বোধ হয়, সহজবোধ্য নয় বলেই বাংলার পণ্ডিতসমাজে এ গ্রন্থের পঠন-পাঠন ছিল না। এ গ্রন্থ যে দুষ্পাঠ্য, তার প্রমাণ, বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও বলেছেন যে, হর্ষচরিতের ‘অনায়াসে অর্থবোধ জন্মে না।‘ শুধু বাংলার পণ্ডিত কেন, অন্য প্রদেশের পণ্ডিতদেরও ঐ একই মত। মহাকবিচূড়ামণি শংকর, হর্ষচরিতের সংকেত নামক যে ব্যাখ্যা লিখেছেন, তা এই বলে শেষ করেছেন–
দুর্বোধে হর্ষচরিতে সম্প্রদায়ানুবোধত্।
গূঢ়ার্থোন্মুদ্রণাং চক্রে শংকরো বিদুষাং রুতে।।
অর্থাৎ হর্ষচরিতের ব্যাখ্যাও আমাদের জন্য লেখা হয় নি, লেখা হয়েছিল ‘বিদুষাং কৃতে’; ফলে এ মহাপুরুষের চরিত ‘শ্রোতুং’ আমাদের কৌতূহল থাকলেও সে কৌতূহল চরিতার্থ করবার সুযোগ আমাদের ছিল না।
৩.
আমাদের মহা সৌভাগ্য এই যে, উক্ত উভয় গ্রন্থই ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়েছে, এবং সেই দুখানি ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে শ্ৰীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় একখানি নব-হর্ষচরিত রচনা করেছেন।
তাঁর রচিত হর্ষচরিত আমরা অবলীলাক্রমে পড়তে পারি, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে এ গ্রন্থ রচনা করেন নি। বহু পরিশ্রম করে তাকে তা রচনা করতে হয়েছে। প্রথমতঃ, বাণভট্টের ইংরেজি তরজমাও সুপাঠ্য নয়। তার পর বাণভট্ট লিখেছিলেন কাব্য, সুতরাং সমস্ত কাব্যখানিই তাঁর মনঃকল্পিত কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। কেননা, স্বয়ং বাণভট্টই তার রচিত কাদম্বরীর গোঁড়াতেই লিখেছেন যে—
অলব্ধবৈদগ্ধ্যবিলাসমুগ্ধয়া ধিয়া নিবন্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা।
অর্থাৎ যদিচ তাঁর কোনোরূপ বৈদগ্ধ্য ছিল না, তবুও তিনি শখের বশীভূত হয়ে কাদম্বরী নামক ‘অতিদ্বয়ী’ কথা একমাত্র মন থেকে গড়েছেন। অতিদ্বয়ী কথা’র অর্থ সেই কথা যা বাসবদত্তা ও বৃহৎকথাকে অতিক্রম করে। এ হেন চরিত্রের লেখকের কোনো কথার উপর আস্থা রেখে ইতিহাস লেখা চলে না, কেননা, ইতিহাসের কথা মনগড়া কথা নয়। অথচ বাণভট্টের কথা প্রত্যাখ্যান করাও চলে না। কারণ, হর্ষের বালচরিত একমাত্র বাণই বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে রাধাকুমুদবাবুকে বাণভট্টের প্রতি কথাটি যাচিয়ে নিতে হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় যাকে inscription বলে, তাই হচ্ছে ইতিহাসের কষ্টিপাথর। হর্ষের বিষয়ে ইসক্রিপশনও আছে, আর সেইসব ইন্সক্রিপশনের সাহায্যে তিনি যাচিয়ে দেখেছেন যে, বাণভট্টের হর্ষচরিত অক্ষরডম্বর হলেও কেবলমাত্র ধ্বনিসার নয়। তার প্রায় প্রতি কথাই সত্য, সুতরাং নির্ভয়ে এ কবির কাব্য ইতিহাসের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। আর হিউয়েন সাংএর কথা যে ইতিহাস, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কেননা, তার ভ্রমণবৃত্তান্তকে কোনো হিসাবেই কাব্য বলা চলে না। ও-গ্রন্থ হচ্ছে একাধারে হিস্টরি ও জিয়োগ্রাফি।
৪.
রাধাকুমুদবাবু তার নব-হর্ষচরিত রচনা করেছেন ইংরেজি ভাষায়; আমি সেই গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করব। কিন্তু প্রথমেই একটু মুশকিলে পড়েছি। সেকালে অজ্ঞাতকুলশীল কোনো কবি বলেছেন–
হেম্নো ভারশতানি বা মদমুচাং বৃন্দানি বা দন্তিনাং
শ্রীহর্ষেণ সমর্পিতানি গুণিনে বাণায় কুত্ৰাদ্য তৎ।
যা বাণেন তু তস্য সূক্তিবিসরৈরুট্টঙ্কিতাঃ কীর্তয়-
স্তাঃ কল্পপ্রলয়েহপি যান্তি ন মনাষ্মন্যে পরিম্নানতাম্। (সুভাষিতাবলী ১৮০)
এ শ্লোকের নির্গলিতাৰ্থ হচ্ছে এই যে, শ্রীহর্ষ বাণভট্টকে যে-ধনদৌলত দিয়েছিলেন, আজ তা কোথায়? অপর পক্ষে বাণভট্ট শ্রীহর্ষের যে কীর্তিকলাপ উট্টঙ্কিত করেছেন, তা কল্পান্তেও ম্লান হবে না।
শ্রীহর্ষ বাণভট্টকে কি সোনারুপে হাতিঘোড়া দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। কিন্তু বাণ যে হর্ষের বিশেষ কিছু কীর্তিকলাপ বর্ণনা করেছেন, তাও নয়। হর্ষচরিত একখানি অদ্ভুত বই। এই অষ্টাধ্যায়ী ইতিহাসের প্রথম দু অধ্যায় বাণচরিত, আর শেষ দু অধ্যায় হর্ষচরিত। বাণভট্ট রাজসভায় উপস্থিত হয়ে প্রথম এই কথা বলে আত্মপরিচয় দেন—
ব্রাহ্মণোহস্মি জাতঃ সোমপায়িনাং বংশে বাৎস্যায়নানাম্।
তার পর আছে নিজের গুণকীর্তন। এ কবির নিজের আভিজাত্য ও বিদ্যার এতদূর গর্ব ছিল যে, তিনি ঐ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের অনেক অংশ নিজের বংশের ও নিজের কথায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ও-কাব্য থেকে রাজচরিত উদ্ধার করা ঢের বেশি লোভনীয় ও সহজ। কিন্তু সে লোভ এখন আমি সংবরণ করতে বাধ্য, নইলে হর্ষচরিত লেখা হবে না। বারান্তরে বাণচরিত বর্ণনা করব, কারণ, তা করা আমার আয়ত্তের মধ্যে। বাণচরিত লিখতে কোনো চৈনিক গ্রন্থ কিংবা শিলালিপির সাহায্য নিতে হবে না।
৫.
কথাসাবিঘাতেন কাব্যাংশস্য চ যোজন।
এ জ্ঞান সংস্কৃত কবিদেরও ছিল। তবে বাণভট্ট বোধ হয় মনে করতেন যে, হর্ষচরিতের কথায় কোনো রস নেই, তাতে যা কিছু রস আছে, সে তাঁর লেখায়। সুতরাং উক্ত গ্রন্থে কথাবস্তু অতি যৎসামান্য।
অপর পক্ষে রাধাকুমুদবাবু লিখেছেন ইতিহাস। সুতরাং বাণভট্টের রচনার ফুলপাতা বাদ দিয়ে তার কথাবস্তুর উপরই তার হর্ষচরিত রচনা করতে হয়েছে। আর-এক কথা : বাণভট্ট যখন হর্ষচরিত শেষ করেছেন, তখন হর্ষের ম্যাটি কুলেশন দেবার বয়স হয় নি। সুতরাং সে-চরিতের অন্তরে ঐতিহাসিক মাল অতি কম, আর কাব্যের মসলাই বেশি। অথচ এ গ্রন্থ উপেক্ষা করে হর্ষচরিতের প্রথম ভাগ লেখা অসম্ভব। আমি রাধাকুমুদবাবুর পদানুসরণ করে শ্রীহর্ষের বাল্যজীবন বাংলায় বলব, শুধু বাণভট্টের যেসব কথা তিনি ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, আমি সেসব যথাসম্ভব বাণভট্টের নিজের কথাতেই বলব। এ কথা শুনে ভয় পাবেন না। হর্ষচরিত অতি দুর্বোধ হলেও বাণভট্ট কাজের কথা অতি সংক্ষেপে সহজবোধ্য সংস্কৃত ভাষাতেই বলেন। তা ছাড়া এ লেখার গায়ে একটু সেকেলে গন্ধও থাকা চাই।
পুরাকালে ভারতবর্ষে শ্ৰীকণ্ঠ নামে একটি দেশ ছিল, এবং সেই দেশে স্থাণ্বীশ্বর নামক জনপদের রাজবংশে শ্রীহর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। এ বংশ পুষ্পভূতির বংশ বলে বিখ্যাত। এই বংশে প্রভাকরবর্ধন নামে একটি রাজা নিজবাহুবলে নানা দেশ জয় করে পরমভট্টারক উপাধি লাভ করেন। তিনি ‘প্রতাপশীল’ এই অপর নামেও বিখ্যাত। তিনি হয়ে উঠেছিলেন–
হূনহরিণকেশরী সিন্ধুরাজজ্বরো,
গুর্জরপ্রজাগরঃ গান্ধারাধিপগন্ধদ্বিপকূটপাকলঃ
লাটপাটপাটচ্চরঃ মালবলক্ষ্মীলপরশুঃ।
বাণভট্ট এসব শব্দযোজনা সত্যের খাতিরে কি অনুপ্রাসের খাতিরে করেছেন, বলা কঠিন।
৬.
যদিও তাঁর কথা সত্য হয় তো সে সত্য অনুপ্রাসের ভারে চাপা পড়েছে। প্রভাকরবর্ধন হনহরিণের কেশরী, সিন্ধুরাজের জ্বর, গুঞ্জরের অনিদ্রা, গান্ধাররাজরূপ গন্ধহস্তীর পিত্তর, লাটচোরের উপর বাটপাড়, ও মালবলক্ষ্মীলতার কুঠার। অর্থাৎ উপরি-উক্ত রাজ্য সব তিনি জয় করুন আর না করুন, ও-সকল রাজ্যের রাজারা তার ভয়ে কম্পান্বিত ছিল। বলা বাহুল্য, এসব দেশ উত্তরাপথের পশ্চিমখণ্ড।
শ্রীহর্ষ প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ৫৯০ খৃস্টাব্দে মহারানী যশোবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধন তার চাইতে বছর চারেকের বড়, এবং তার ভগ্নী রাজ্যশ্রী বছর দুয়েকের ছোট।
বাণভট্ট কাদম্বরীর রাজকুমার চন্দ্ৰাপীড় কোথায়, কি কি শাস্ত্রে, কি ভাবে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছিলেন, তার লম্বা বর্ণনা করেছেন; কিন্তু হর্ষবর্ধনের শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে তিনি একেবারে নীরব। শুধু রাজকুমারদ্বয়ের কে কে অনুচর ছিলেন, সেই কথা বাণ আমাদের বলেছেন।
রাজ্যশ্রীর জন্মের পর প্রভাকরবর্ধন, রানী যশোবতীর ভ্রাতুস্পুত্র–
ভণ্ডিনামানমনুচরং কুমারয়োরপিতবান্।
এই ভণ্ডিই ক্ষেত্রে, কি মন্ত্রণাগৃহে, প্রথমে রাজ্যবর্ধনের পরে শ্রীহর্ষের প্রধান সহায় ছিলেন।
কিছুকাল পরে প্রভাকরবর্ধন মালবরাজের পুত্র কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে কুমারদ্বয়ের অনুচর করেছিলেন। এই মাধবগুপ্তই পরে হর্ষবর্ধনের অতি অন্তরঙ্গ মুহৃৎ হন।
কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত যে hostage স্বরূপে প্রভাকরবর্ধনের নিকট রক্ষিত হয়েছিলেন, এ রকম অনুমান করা অসংগত নয়। কারণ, প্রভাকরবর্ধন ছিলেন মালবলক্ষ্মীলতার পরশু।
কিন্তু ভণ্ডি কে? তিনি ছিলেন রানী যশোবতীর ভ্রাতুস্পুত্র। কিন্তু যশোবতী কার কন্যা, সে বিষয়ে বাণভট্ট সম্পূর্ণ নীরব; যদিচ তিনি রাজারানীদের কুলের খবর বিশেষ করে রাখতেন।
৭.
কালক্রমে রাজ্য বিবাহযোগ্য হলেন। যখন তার বিবাহ হয়, তখন তিনি বালিকা কিংবা কিশোরী, বাণভট্ট সে কথা খুলে বলেন নি। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তার থেকে অনুমান করা যায় যে, একালে সারদা আইনে সে বিবাহ বাধত।
একদিন প্রভাকরবর্ধন বাহকক্ষস্থ কোনো পুরুষ কর্তৃক গীয়মান বক্ষ্যমাণ আর্যাটি শুনলেন—
উদ্বেগমহাবর্তে পাতয়তি পয়োধরোন্নমনকালে।
সরিদিব তটমনুবর্ষ বিবর্ধমানা সুতা পিতরম্।।
এই গানটি শোনবামাত্র তিনি যশশাবতীকে সম্বোধন করে বললেন–
দেবি তরুণীভূত বৎসা রাজ্যশ্ৰীঃ।
অতএব আর কালবিলম্ব না করে ওর বিবাহ দেওয়া কর্তব্য।
এর পরেই প্রসিদ্ধ মৌখরী-বংশের তিলকস্বরূপ কান্যকুজের রাজা অবন্তিবর্মার জ্যেষ্ঠপুত্ৰ গ্ৰহবর্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হল। এ বিবাহ খুব ঘটা করে দেওয়া হয়েছিল, কেননা বাণভট্ট খুব ঘটা করে তার বর্ণনা করেছেন। দুঃখের বিষয়, বিবাহ-উৎসব ও বিবাহমণ্ডপের সাজসজ্জার বর্ণনা ভালো বোঝা যায় না। বিবাহমণ্ডপ–
স্ফুরদ্ভিরিন্দ্ৰায়ুধসস্রৈরিব সংছাদিতম্।
কিসের দ্বারা?–
ক্ষৌমৈশ্চ বাদরৈশ্চ দুকুলৈশ্চ লালাতন্তুজৈশ্চাংশুকৈশ্চ নেত্রৈশ্চ
নির্মোকনিভৈরকঠোররম্ভাগর্ভকোমলৈনিশ্বাসহাযৈঃ স্পর্শানুমেয়ৈর্বাসোভিঃ।
এসব জিনিস কি? টীকাকার বলেন, বস্ত্রবিশেষ; অভিধানেও এর বেশি কিছু বলে না। তবে আমরা এই পর্যন্ত অনুমান করতে পারি যে, ‘বাদর’ খদ্দর নয়, কেননা, বাদরের রূপ ইন্দ্রধনুর, আর তা ফুয়ে উড়ে যায়, নাহয় তো দেখতে সাপের খোলসের মত আর অকঠোররম্ভাগৰ্ভকোমল। সংক্ষেপে এসব কাপড় এত মিহি যে, তারা কেবলমাত্র স্পর্শানুমেয়। এ বর্ণনা থেকে এইমাত্র জানা যায় যে, হর্ষযুগের ভারতবর্ষ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের দেশ ছিল না। বাণভট্টের হর্ষচরিত থেকে, রাজারাজড়াদের না হোক, অন্নবস্ত্রের ইতিহাস উদ্ধার করা সহজ।
এর কিছুদিন পরে রাজা প্রভাকরবর্ধন হনপশুদের বধ করবার জন্য রাজ্যবর্ধনকে উত্তরাপথে পাঠিয়েছিলেন। হর্ষবর্ধনও হিমালয়ের উপকণ্ঠে বাঘভালুক শিকার করতে গেলেন। বলা বাহুল্য যে, হর্ষদেব–
স্বল্পীয়োভিরেব দিবসৈনিঃশ্বাপদারণ্যানি চকার।
এমন সময়ে তিনি খবর পেলেন যে, প্রভাকরবর্ধন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন, এবং পরদিনই তার পিতার মৃত্যু হল ও রানী যশোবতী সহমরণে গেলেন।
তার পর রাজ্যবর্ধন দেশে ফিরে এসে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন; কারণ, পূর্ব হতেই সংসার ত্যাগ করবেন বলে তিনি মন স্থির করেছেন, উপরন্তু পিতৃশোক তাকে একান্ত কাতর করে ফেলেছে। রাজ্যবর্ধন স্পষ্টই বললেন যে–
স্ত্রিয়ো হি বিষয়ঃ শুচাম্। তথাপি কিং করোমি। স্বভাবস্য সেয়ং কাপুরুষতা বা স্ত্রৈণং বা যদেবমাস্পদং পিতৃশোকহুতভুজো জাতোহস্মি।
কিন্তু হর্ষ কিছুতেই বড় ভাইকে টপকে সিংহাসনে চড়ে বসতে সম্মত হলেন না।
৮.
শোকবিমূঢ় ভ্রাতৃদ্বয় কিংকর্তব্য স্থির করতে পারছেন না, এমন সময় রাজ্যশ্রীর সংবাদক নামক পরিচারক এসে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলে
যেদিন অবনীপতির মৃত্যুর সংবাদ এল, সেই দিনই দুরাত্মা মালবরাজ গ্রহবর্মাকে বধ করে রাজ্যশ্রীর পায়ে বেড়ি পরিয়ে কান্যকুজের কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।
এ-সংবাদ শুনে রাজ্যবর্ধমের হৃদয়ে শোকাবেগের পরিবর্তে রোষাবেগ স্থান লাভ করলে, ও তিনি হর্ষকে সম্বোধন করে বললেন—
এ রাজ্য তুমি পালন করে। আমি আজই মালবরাজকুলের ধ্বংসের জন্য যাত্রা। করছি। একমাত্র ভণ্ডি দশ সহস্র অশ্ব-সৈন্য নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।
হর্ষও এ কথা শুনে বললেন, আমিও তোমার অনুগমন করতে প্রস্তুত–
যদি বাল ইতি নিতরাং তহি ন ত্যাজ্যোহস্মি। অশক্ত ইতি ক্ব পরীক্ষিতোহস্মি। কিন্তু রাজ্যবর্ধন এ পরীক্ষা করতে স্বীকৃত হলেন না, বালক হর্ষকে ত্যাগ করে একাই যুদ্ধযাত্রা করলেন।
এর ক দিন পরেই কুন্তল নামক অশ্ববার এসে সংবাদ দিলে যে, রাজ্যবর্ধন মালব-সৈন্যের উপর জয়লাভ করবার পর–
গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাসং মুক্তশস্ত্ৰমেকাকিনং বিশ্রং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতম্–
ঐ গৌড়াধিপের নাম শশাঙ্ক। এ সংবাদ শুনে প্রভাকরবর্ধনের বৃদ্ধ সেনাপতি হর্ষকে বললেন—
কিং গৌড়াধিপেনৈকেন। তথা কুরু যথা নান্যোহপি কশ্চিদাচরত্যেবং ভূয়ঃ।
হর্ষদেব উত্তর করলেন—
শ্রূয়তাং মে প্রতিজ্ঞা
পরিগণিতৈরেব বাসরৈনির্গৌড়াং করোমি মেদিনীম্।
তার পর অবন্তি নামক মহাসন্ধিবিগ্রহকারককে আদেশ করলেন যে, উদয়াচল হতে অস্তগিরি পর্যন্ত সকল দেশের সকল রাজাদের কাছে এই মর্মে ঘোষণাপত্র পাঠাও যে—
সর্বেষাং রাজ্ঞাং সজ্জীক্রিয়ন্তাং করাঃ করদানায় শস্ত্ৰগ্ৰহণায় বা।
এর পরেই তিনি মান্ধাতা-প্রবর্তিত দিগ্বিজয়ের পথ অবলম্বন করলেন।
৯.
হর্ষদেব হাতিঘোড়। লোকলস্কর নিয়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হবেন, এমন সময়–
ভণ্ডিরেকেনৈব বাজিনা কতিপয়-কুলপুত্ৰপরিবৃতে রাজদ্বারমাজগাম।
ভণ্ডির পরিধানে মলিন বাস আর সর্বাঙ্গ শত্রুশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। হর্ষ ভণ্ডির কাছে প্রাতৃমরণবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন এবং ভণ্ডিও আগাগোড়া সকল কথা বললেন। তার পর নরপতি জিজ্ঞাসা করলেন, রাজ্যশ্রীর অবস্থা কি? ভণ্ডি উত্তর করলেন, রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর দেবী রাজা শ্রী কুশস্থলে গুপ্ত কর্তৃক গৃহীত হন, পরে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সপরিবারে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করেছেন, এ কথা আমি লোকমুখে শুনেছি, এবং তার খাজে বহু লোক পাঠিয়েছি; কিন্তু তারা কেউ ফিরে আসে নি।
এ কথা শুনে হর্ষ বললেন, অন্য লোকের কি প্রয়োজন? অন্য কর্ম ত্যাগ করে যেখানে রাজ্যশা আছেন সেখানে স্বয়ং আমি যাব, আর তুমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে গৌড়াভিমুখে গমন করো।
এর পর হর্ষ মালবরাজকুমার মাধবগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করলেন, এবং বৌদ্ধভিক্ষু দিবাকর মিশ্রের আশ্রমে রাজ্যশ্রীর সাক্ষাৎ পেলেন। যখন হর্ষ দিবাকর মিশ্রের আশ্রমে উপস্থিত হলেন তখন রাজ্যশ্রী চিতায় প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন। হর্ষ ও দিবাকর মিশ্র তাকে আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত করলেন। রাজা বৌদ্ধভিক্ষুণীর ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য দিবাকর মিশ্রের কাছে প্রার্থনা জানালেন। দিবাকর মিশ্র সে প্রার্থনা মঞ্জুর করতে স্বীকৃত হলেন না দু কারণে। প্রথমতঃ রাজ্যশ্রীর বয়স অল্প, দ্বিতীয়তঃ সে শোকগ্রস্ত। তার পর হর্ষ যখন ভগ্নীকে কথা দিলেন যে, তিনিও ভ্রাতৃমরণের প্রতিশোধ নিয়ে পরে কাষয়বসন ধারণ করবেন, তখন রাজ্যশ্রী সে কটা দিন অপেক্ষা করতে স্বীকৃত হলেন।
এইখানেই বাণভট্টের হর্ষচরিত শেষ হল।
১০.
বাণভট্ট যে কেন এইখানেই থামলেন, তা আমাদের অবিদিত, এবং তা জানবারও কোনো উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু নানারূপ অনুমান করতে পারি, কিন্তু সেসব অনুমানের হর্ষচরিতে কোনো অবসরও নেই, সার্থকতাও নেই। তবে যে কারণেই হোক, তিনি যে আট অধ্যায়কে অষ্টাদশ করেন নি, এ আমাদের মহা সৌভাগ্য। কারণ, ও-ধরনের লেখা এর বেশি আর পড়া অসাধ্য। ইংরেজিতে বলে life is short; সুতরাং আর্ট যদি অতি লম্বা হয় তো এক জীবনে তার চর্চা করে ওঠা যায় না।
সে যাই হোক, বাণভট্ট হিস্টরি লেখেন নি, লিখেছেন হর্ষের বায়োগ্রাফি। জীবনচরিত লেখবার আর্ট একরকম portrait paintingএর আর্ট। এ আর্টের বিষয় বা ঘটনা নয়। এর একমাত্র বিষয় হচ্ছে একটি মানুষ। মানুষের বাইরের চাইতে অন্তরই জীবনচরিত-লেখকের মনকে বেশি টানে। ফলে এর থেকে সেকালের রাজারাজড়াদের ইতিহাস উদ্ধার করা অসম্ভব।
হর্ষ যে দিগবিজয় করেছিলেন তার প্রমাণ তিনি ‘সকল উত্তরাপথেশ্বর’ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দিগ্বিজয়ের বিবরণ হর্ষচরিতে নেই, হিউয়েন সাংএর ভ্রমণবৃত্তান্তেও নেই।
হর্ষচরিত থেকে আমরা এই মাত্র জানতে পাই যে, প্রভাকরবর্ধন লাট সিন্ধু গান্ধার ও মালবদেশের রাজাদের শত্রু ছিলেন এবং তার মৃত্যুর পরেই মালবরাজ কান্যকুক্ত আক্রমণ করে গ্রহবনাকে বধ করেন। কিন্তু এ মালবরাজ যে কে, হর্ষচরিতে তার নাম নেই। ভণ্ডি বলেছেন গুপ্তনামা, এর বেশি কিছু নয়।
রাধাকুমুদবাবু প্রমাণ পেয়েছেন, এ গুপ্ত হচ্ছে দেবগুপ্ত, এবং তিনি ছিলেন হর্ষের সহচরদ্বয় মাধবগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রাজ্যবর্ধন একে পরাভূত ক’রে কান্যকুজরাজ্য উদ্ধার করেন, এবং হর্ষ এই ভগ্নীপতির সিংহাসন অধিকার করেন।
১১
এখন, এই ভণ্ডি নামক ব্যক্তিটি কে? তিনি যে হর্ষবর্ধনের প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজবর্ধনের মৃত্যুর পর যখন অপরাপর মন্ত্রীরা হর্ষকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করতে ইতস্ততঃ করছিলেন, তখন ভণ্ডির পরামর্শেই তারা বালক হর্ষকে রাজা করেন। মালবরাজের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্ধন যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন ভণ্ডিই দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে। তাঁর অনুগমন করেন এবং সে-যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর ভণ্ডিই হর্ষের আদেশে গৌড়াধিপ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান। সুতরাং তিনিই যে হর্ষদেবের friend, philosopher and guide ছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসংগত নয়। এই কারণেই ভণ্ডি লোকটি কে, জানবার জন্য কৌতূহল হওয়া ঐতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক।
বাণভট্ট এইমাত্র বলেছেন যে, ভণ্ডি যশোবতীর ভ্রাতুস্পুত্র। কিন্তু যশোবতী যে কার কন্যা ও কার ভগ্নী, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব।
রাধাকুমুদবাবু বলেন যে, যশোবতী হুনারি যশোবর্মনের কন্যা। যশোেবন। যে-সে রাজা নন। ঘূনরাজ মিহিরকুলকে যুদ্ধে পরাভূত করে তিনি ভারতবর্ষ নিতুন করেন, এবং এক দিকে ব্ৰহ্মপুত্র হতে পশ্চিমসমুদ্র ও আর-এক দিকে হিমালয় হতে মহেন্দ্রপর্বত পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট হন। যশোবতী এ হেন রাজচক্রবর্তীর কন্যা হলে বাণভট্ট সে কথা গোপন করতেন না। আর যশোবর্মনের পুত্র শিলাদিত্যই নাকি ভণ্ডির পিতা, যে রাজার বিরুদ্ধে ল’ড়ে ভণ্ডি ও রাজ্যবর্ধন জয়লাভ করেন। রাধাকুমুদবাবু যা বলেছেন, তা হতে পারে। কিন্তু এ বংশাবলী আকে মেলে না। যশোবন হূন নিপাত করেছিলেন ৫২৮ খৃস্টাব্দে আর হষের জন্ম হয় ৫৯০ খৃস্টাব্দে; সুতরাং বিয়ের সময়ে যশোবতীর বয়সে কত ছিল? সেকালে রাজারাজড়াদের ঘরের মেয়েদের কোন্ বয়সে বিয়ের ফুল ফুট৩, তা রাজ্যশ্রীর বিবাহ থেকেই জানা যায়। সুতরাং ভণ্ডি যে যশোবমণের পৌত্র, এ অনুমান প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।
১২.
তারিখ না থাকলে ইতিহাস হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাস জানা একরকম অসম্ভব, কারণ সংস্কৃত সাহিত্য তারিখছুট। সেইজন্যই আমাদের দেশের কোনো ব্যক্তির অথবা কোনো ঘটনার তারিখ জানতে হলে বিদেশে যেতে হয়। চীনে লেখকদের মহাগুণ এই যে, তাদের সকলেরই মহাকালের না হোক, ইহকালের জ্ঞান ছিল। ভাগ্যিস হিউয়েন সাং এ দেশে এসেছিলেন, তাই আমরা হর্ষবর্ধনের সঠিক কালনির্ণয় করতে পারি। উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে ও কতকটা ইন্সক্রিপশনের সাহায্যে আমরা জানি যে, হর্ষ জন্মেছিলেন ৫৯০ খৃস্টাব্দে, রাজা হয়েছিলেন ৬০৬ খৃস্টাব্দে, আর তার মৃত্যু হয়েছিল ৬৪৮ খৃস্টাব্দে।
তারিখ বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না, একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস ছাড়া। কিন্তু তাই বলে ইতিহাস মানে প্রাচীন পঞ্জিকামাত্র নয়; এমনকি, রাজরাজড়ার জীবনচরিতও নয়। আমরা একটা বিশেষ দেশের, বিশেষ কালের, বিশেষ সমাজের মতিগতি সব জানতে চাই। কিন্তু সে জ্ঞান লাভ করবার মালমসলা হর্ষচরিতেও নেই, হিউয়েন সাংএর ভ্রমণবৃত্তান্তেও নেই। রাধাকুমুদবাবু হর্ষচরিত লিখেছেন Rulers of India নামক সিরিজের জন্য। সুতরাং হর্ষের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাকে একটি পুরো অধ্যায় লিখতে হয়েছে। কিন্তু এ অধ্যায়টি তাকে এই অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে যে, হর্ষযুগের রাজশাসন তার পূর্ববর্তী গুপ্তযুগের অনুরূপ; সুতরাং তিনি এ বিষয়ে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা গুপ্তযুগের বিবরণ–যদিও হর্ষের রাজ্য গুপ্তরাজ্যের মত নিরুপদ্রব ছিল না। হিউয়েন সাংকে বহুবার চোরডাকাতের হাতে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু ফা-হিয়েনের কেউ কেশস্পর্শ করে নি। হর্ষের পূর্বে দেশ অরাজক হয়ে পড়েছিল, আর হর্ষের মৃত্যুর পর আবার অরাজক হয়েছিল। ইতিমধ্যে যে তিনি দেশকে সম্পূর্ণ সুশাসিত করতে পারেন নি, এতে আর আশ্চর্য কি?
১৩.
আমি পূর্বে বলেছি যে, রাধাকুমুদবাবু তার হর্ষচরিত লিখেছিলেন রুলস অব ইণ্ডিয়া নামক ইংরেজি সিরিজের দেহ পুষ্ট করবার জন্য। এ সিরিজের নামাবলী পড়ে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের শাসনকর্তা কখনো ভারতবাসী হয় না, হয় শুধু বিদেশি। একমাত্র অশোক এ দলে স্থানলাভ করেছেন। ফলে অশোক যে বিদেশি, তাই প্রমাণ করতে এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা উঠে-পড়ে লেগেছেন। রাধাকুমুদবাবু হর্ষকেও এই ছত্রপতি রাজাদের দলভুক্ত করেছেন। সুতরাং দু দিন পরে হয়তো শুনব যে, অশোক যেমন পারসিক, হর্ষ তেমনি হূন। হর্ষের মাতুলপুত্র হচ্ছেন ভণ্ডি, এবং হূন ভাষার পণ্ডিতরা বলেন যে, ভণ্ডি নাম হূন নাম। তা যদি হয় তো হর্ষের মাতৃকুল যে হূন-কুল, এ অনুমান করা ঐতিহাসিক পদ্ধতি-সংগত।
যদি ধরে নেওয়া যায় যে, অশোক সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষ তিনজনই স্বদেশি রাজা ছিলেন, তাহলে এ তিনজন যে কি করে রাজা থেকে মহারাজাধিরাজ হয়ে উঠলেন, তার একটা হিসেব পাওয়া যায়।
ভারতবর্ষ চিরকালই নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল; অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে ইউনিটারি গবর্মেন্ট, এত প্রকাণ্ড দেশে সে জাতীয় গবর্মেন্ট স্বাভাবিক নয়। যখনই কোনো প্রবল বিদেশি শত্রুর হাত থেকে ভারতবাসীদের পক্ষে আত্মরক্ষা করবার প্রয়োজন হয়েছে, এবং যে রাজা সে বহিঃশত্রুর কবল থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন, তখনই তিনি, সমগ্র ভারতবর্ষের না হোক, উত্তরাপথের সম্রাট হয়েছেন। গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দারের ভারতবর্ষের ব্যর্থ আক্রমণের অব্যবহিত পরেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অশোক হচ্ছেন তার পৌত্র। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত শকারিবিক্রমাদিত্য। এবং যেকালে দেশ থেকে হূন-পশু বহিষ্কৃত হয়, সেই কালেই হর্ষবর্ধন সকল উত্তরাপথেশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। যবনদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করবার জন্য মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা। শকদের কবল থেকে পশ্চিমভারত উদ্ধার করবার ফলেই গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা। আর হূন-হরিণ-কেশরী বলেই হর্ষ দেশের পরমেশ্বর হয়েছিলেন। অর্থাৎ একমাত্র বিদেশিই ভারতবর্ষের ruler হয় না–বিদেশির হাত থেকে যে দেশরক্ষা করতে পারে, সেও সেকালে ভারতবর্ষের ruler হত। মেধাতিথি আর্যাবর্ত নামক দেশের এই বলে পরিচয় দিয়েছেন–
আর্যা বর্তন্তে তত্র পুনঃ পুনরুদ্ভবস্ত্যাক্রম্যাক্রম্যাপি তত্র ন চিরং ম্লেচ্ছাঃ স্থাতারে। ভবন্তি।
এই উত্থানপতনের ইতিহাসই ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস।
১৪
বাণভট্ট হূনদের বরাবর হূন-হরিণী ব’লে এসেছেন; কিন্তু তারা ঠিক হরিণ-জাতীয় ছিল না, না রূপে, না গুণে। হূনরা ছিল হিংস্র বনমানুষ। ভিসেন্ট স্মিথ বলেন–
Indian authors having omitted in give any detailed description of the savage invaders who ruthlessly oppressed their country for three quarters of a century, recourse must be had to European writers to obtain a picture of the devastation wrought and the terror caused to settled communities by the fierce barbvarians.
হূন নামক যে ঘোর নৃশংস বর্বর জাতি পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, সেই জাতিরই একটি বিশেষ শাখা পারস্যদেশ ও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। সুতরাং ইউরোপের লোক তাদের যে বর্ণনা করেছে, তার থেকে আমরা হূনদের রূপগুণের পরিচয় পাই। স্মিথ বলেন–
The original accounts are well summarised by Gibbon:
The numbers, the strength, the rapid motions and the implacable cruelty of the Huns, were felt and dreaded and magnified by the astonished Goths, who beheld their fields and villages consumed with flames and deluged with indiscriminate slaughter. To these real terrors, they added the surprise and abliorrence which were excited by the slurill voice, the unčouth gestures, and the strange deformity of the Huns. They were distinguished from the rest of the human species by their broad sloulders, flat wioses and small black eyes, deeply buried in their hiad; and as they were almost destitute of beards, they never enjoyed thie manly graces of youth or the venerable aspect of age.
যে হূনরা ইউরোপ আক্রমণ করেছিল, তাদেরই জাতভাইরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল, সুতরাং রূপে ও চরিত্রে তারা যে পূর্বোক্ত হূনদের অনুরূপ ছিল, এরূপ অনুমান করা অসংগত নয়। তারা যে ঘোর অসভ্য ও ঘোর নৃশংস নরপশু, শুনতে পাই, এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যও সাক্ষ্য দেয়।
এ দেশে যাঁরা আসেন, ইউরোপীয়রা তাদের White Huns বলেন; কি কারণে, তা জানি নে। কিন্তু তারা যে কৃষ্ণকায় ছিলেন না, তার প্রমাণ বক্ষ্যমাণ সংস্কৃত পদে পাওয়া যায়।
সদ্যো মুণ্ডিতমত্তহূনচিবুক প্ৰস্পর্দ্ধি নারঙ্গকম্।
এ উপমা থেকে এই জানা যায় যে হূনের রং ছিল হলদে, ও তাদের চিবুক ছিল almost destitute of beards। কারণ, তাদের যে নামমাত্র দাড়ি ছিল, তা কামালে মাতাল হৃনের চিবুক নারঙ্গের রূপ ধারণ করত।
এই কিম্ভুতকিমাকার জাতির আচারব্যবহারও অতিশয় কদর্য ছিল। হিন্দুর মত শুদ্ধাচারী জাতির পক্ষে এ কারণেও হূনজাতি অসহ্য হয়েছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং তার ভ্রমণবৃত্তান্তে এ কথা উল্লেখ করেছেন।
সুতরাং হূনদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে একটা মারাত্মক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হবার স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষকে এ রোগের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাকে যে দেশের লোক মহাপুরুষ বলে গণ্য করবে, এতে আশ্চর্য কি?
১৫
ভারতবর্ষ সেকালে ছিল নানা রাজার দেশ। সুতরাং রাজায় রাজায় যুদ্ধ ছিল সেকালে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু কোন্ রাজা কাকে মারলে, তাতে সমাজের বেশি কিছু যেত আসত না। মনুর বিধান আছে যে–
জিত্ব সম্পূজয়েবোন্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্মিকান্।
প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানি চ।।
সর্বেষান্তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীষিতম্।
স্থাপয়েৎ তত্র তদ্বংশং কুর্য্যাৎ চ সময়ক্রিয়াম্। (মনু। ৭ অধ্যায় ২০১-২০২ শ্লোক)
উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয়ের মেধাতিথিকৃত ভাষ্যানুবাদ—
বিজয়ী রাজা পররাজ্য জয় করবার পর পুরী ও জনপদের প্রশমন করে, তত্রস্থ দেবদ্বিজ ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের রণার্জিত ধনের চতুর্থাংশ ও ধূপদীপগন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করবেন। তার পর সে দেশের গৃহস্থ ব্যক্তিরা যাতে কোনোরূপ কষ্টে না পড়ে, তজ্জন্য তাদের এক বৎসর কিংবা দু বৎসরের কর ও শুল্কপ ভার থেকে মুক্তি দেবেন, যাতে তাদের জীবনযাত্রার কোনোরূপ ব্যাঘাত না হয়। তার পর নগরের ও জনপদের অভয়দান করবেন, অর্থাৎ ডিণ্ডিম প্রভৃতির দ্বারা থোষণা করবেন যে, যারা পূর্বস্বামীর প্রতি অনুরাগবশতঃ আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের আমি ক্ষমা করলুম, তারা যেন নির্ভয়ে স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে।
বিজিত রাজ্যের জনসাধারণকে পূর্বোক্ত উপায়ে শান্ত ও সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেও বিজয়ী রাজা যদি জানতে পান যে, সে রাজ্যের প্রজাদের পূর্বস্বামীর উপর অনুরাগ অতি প্রবল, এবং তারা কোনো নূতন রাজা ও রাজশাসন চায় না, তাহলেও তিনি সংক্ষেপে প্রজাদের মনোভাবের বিষয় অবগত হয়ে সেই বংশের অপর কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এবং তদ্দেশের সমবেত প্ৰজামণ্ডলী ও রাজপুরুষদের সম্মতিক্রমে ও তাদের সমক্ষে সেই নব অভিষিক্ত রাজার সঙ্গে এই মর্মে সন্ধি করবেন যে, তোমার আয়ের অর্ধেক আমি পাব, এবং তুমি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে সকল বিষয়ে ব্যাকর্তব্য স্থির করবে; আর আমি যদি দৈবক্রমে এবং অকারণে বিপগ্রস্ত হই, তুমি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তোমার অর্থ ও বলের দ্বারা আমার সাহায্য করবে।
মনুর বিধান law নয়, custom; সমাজে যা ঘটত, তারই বিবরণ। সুতরাং সেকালে জয়-পরাজয়ের ফলে রাজা বদলালেও রাজ্য বদলাত না।
অপর পক্ষে শক যবন হূন প্রভৃতির আক্রমণে সমগ্র সমাজ যুগপৎ বিপর্যস্ত ও নিপীড়িত হত। কারণ, এই বিদেশি শত্রুরা দেবদ্বিজ রাজা প্রজা কারও মর্যাদা রক্ষা করতেন না, সকলেরই উপর সমান অত্যাচার করতেন। সুতরাং তুন প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুধু রাজার যুদ্ধ নয়, রাজাপ্রজা উভয়ের মিলিত আত্মরক্ষার প্রয়াস। এ অবস্থায় যখনই হিন্দুরা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে তখনই তাদের আনন্দ আর্টে-সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। হিন্দু-প্রতিভা পরবশ হলেই নিদ্রিত হয়ে পড়ে, আত্মবশ হলেই আবার জাগ্রত হয়।
অশোকের যুগ ভারতবর্ষের স্থাপত্যশিল্পের যুগ। গুপ্তযুগ কালিদাসের কাব্যের ও অজন্তাগুহার চিত্রশিল্পের যুগ। আর হর্ষের যুগ কাদম্বরী ও ভর্তৃহরিশতকের যুগ।
প্রাচীন ভারতের এই চক্রবর্তী মহারাজরা সত্যসত্যই মহাপুরুষ ছিলেন। কারণ, তারা একমাত্র যোদ্ধা ছিলেন না, দেশের সকল প্রকার গুণীর তাঁরা গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন, এবং তাদের সাহায্যেই দেশের কাব্য আর্ট প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধন নিজেরাও আর্টিস্ট ছিলেন। হর্ষ দেশের ধর্ম ও সাহিত্যকে যে কতদূর বাড়িয়ে তুলেছিলেন, তার
পরিচয় রাধাকুমুদবাবুর পুস্তকে সকলেই পাবেন।
১৩৩৭ ভাদ্র
০. প্রবন্ধ সংগ্রহ – ভূমিকা – অতুলচন্দ্র গুপ্ত
বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। রচনার অনতিপরিসর বন্ধনের মধ্যে কোনো বিষয়ে লেখকের বক্তব্যের আলোচনা ও মীমাংসার প্রকাশ প্রবন্ধের মূল অর্থ ও আদি রূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ও তার সমকালে বাংলায় প্রবন্ধের রূপ ছিল মোটের উপর এই অনলংকৃত আদি রূপ–রামমোহন রায়ের ধর্মালোচনায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজসংস্কারের তর্কবিতর্কে, ভূদেব মুখখাপাধ্যায়ের পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধগুলিতে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন নানা রচনার মধ্যে প্রবন্ধরচনায় হাত দিলেন তখন তার সাহিত্যের সোনার কলমে প্রবন্ধের মধ্যে এল বক্তব্যের অতিরিক্ত উপরিপাওনা, যাতে রচনা হয় সাহিত্য। প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠল। সেই অবধি বাংলায় সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধের চলন হয়েছে। বিষয়ের নানাত্বে এবং প্রবন্ধলেখকদের রুচির ও শক্তির তারতম্যে বাংলার প্রবন্ধসাহিত্যে বৈচিত্র্য এসেছে, যেমন এসেছে অন্যসব ভাষায়।
সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধ ভাষা থেকে আটপৌরে নিরাভরণ প্রবন্ধকে বাতিল করে না। ভাষার যা প্রথম কাজ, বক্তব্যকে ব্যক্ত করা, তা চিরকালই থাকবে তার প্রধান কাজ। অনেক বিষয় আছে যাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধের চরম সাফল্য বক্তব্যকে সুব্যক্ত করা। রাঙিয়ে বলা কি সাজিয়ে বলা যেখানে হাস্যকর। অস্থানে কবিত্ব, অর্থাৎ ঔচিত্যজ্ঞানের অভাব। বিজ্ঞান কি ইতিহাসের কোনো তথ্যের সুপরিচয় দিতে যা প্রয়োজন সে হচ্ছে বিষয়ের পূর্ণ পরিচ্ছন্ন জ্ঞান, যে বিচার ও যুক্তিতে তথ্যের প্রতিষ্ঠা তার পারম্পর্যের মীর ধারণা, এবং সে জ্ঞান ও ধারণাকে পাঠকের মনে স্বচ্ছন্দে অবিকৃত পৌঁছে দেবার বাক্যরচনার কুশলতা। অলংকরণ এখানে বোঝা চাপানো। পাঠকের মনের পথে ঝটিতি গতির বাধা। এখানে রচনার যে গুণের প্রয়োজন সে হচ্ছে শুধু প্রসাদগুণ। অবশ্য এ প্রসাদগুণ আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়, সর্বজনসাধ্যও নয়। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষ্যকার-টীকাকারদের মধ্যে যারা প্রথম; শ্রেণীর, তাদের রচনা এ রকম রচনার উৎকৃষ্ট নমুনা। যেমন এ যুগের কোনো কোনো বিজ্ঞানীর শিক্ষিতসাধারণের জন্য রচিত প্রবন্ধ। কখনো হঠাৎ হাতের গুণে এ রচনাও সাহিত্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যের সুপরিচিত রং ও ভূষণে নয়। রচনা থাকে তেমনি নিরাভরণ। বিষয়ের জ্ঞান ও তার প্রতিষ্ঠার প্রণালীর বিশদ বিবরণ দেওয়া ছাড়া রচনার আর-কোনো অবান্তর উদ্দেশ্যও থাকে না। তবুও সে রচনা, কেবল বুদ্ধিকে উক্তি ও তৃপ্ত করে না, মনকেও মুগ্ধ করে। আটপৌরের যা অতিরিক্ত তা বুদ্ধিকে বিষয় ও যুক্তির অনুধাবন থেকে অন্যমনা করে না, জ্ঞান ও বিচারকেই মনে কেটে বসিয়ে দেয়। নিরাবরণ কেজো শরীর অবয়ব-সংস্থানের সুঠামে কেজো থেকেও হয় মনোহারী। ছবিতে রং নেই, কিন্তু রেখাঙ্কনের কৌশল কেবল বস্তুকে আঁকে না, তার অন্তরকেও প্রকাশ করে। শংকরের বেদান্তসূত্রভাষ্যের প্রস্তাবনা এর উদাহরণ। গত শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ সেদিনের নবলব্ধ জ্ঞান সাধারণ্যে প্রচারের জন্য প্রবন্ধ লিখেছেন। তার মধ্যে আচার্য হাক্সলির প্রবন্ধগুলি এ রকম রচনার ভালো উদাহরণ। বিষয় ও উদ্দেশ্যে আটপৌরে হয়েও অসাধারণ। অন্য বিজ্ঞানীদের অনুরূপ প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করলেই প্রভেদ বোঝা যায়। আইন ও তার ইতিহাস বিষয়বস্তুতে নীরস। অধ্যাপক মেইটল্যাণ্ড ইংলণ্ডের আইনের এক ইতিহাস লিখেছেন, এবং সে ইতিহাস নিয়ে ছোট-বড় অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে ও আবিষ্কারে তা পরিপূর্ণ, ঐতিহাসিকের একনিষ্ঠ সত্যভাষণ তার প্রতি পাতায়। কিন্তু এই নীরস উপকরণ মেইটল্যাণ্ডের হাতে পেয়েছে আশ্চর্য গড়ন। কোনো বাহ্যিক উপচারে নয়। নীরসকে সরস করে প্রকাশের অসাধারণ লিপিকৌশলে। মেইটল্যাণ্ডের পূর্বে ইংলণ্ডের আইনের সম্পূর্ণতর ইতিহাস রচনা হয়েছে, যেমন অধ্যাপক হোল্ডসওয়ার্থের ইতিহাস। তথ্য পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শনের আধার। চোখ বুজে নির্ভর করা যায়। কিন্তু মেইটল্যাণ্ডের সঙ্গে তফাত আইনসর্বস্ব পাঠকের কাছেও অজ্ঞাত থাকে না। যে শক্তি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম, আর যে শক্তি কর্মকে আয়ত্ত করেও দশ আঙুল উর্ধ্বে থাকে তাদের যে তফাত। বাংলা প্রবন্ধে এ রকম রচনার বড় দৃষ্টান্ত প্রমথ চৌধুরীর ‘রায়তের কথা। বিগত যুগের ইংরেজ সিবিলিয়ান অ্যাসকলি সাহেব বাংলাদেশের চাষের জমির স্ব-স্বামিদের এক ঐতিহাসিক বিবরণ লিখেছিলেন। পরিষ্কার ঝরঝরে সুপাঠ্য লেখা। বাংলাদেশের রায়তের অবস্থা ও সে-অবস্থার ইতিহাসের বিশদ বর্ণনা। প্রমথ চৌধুরীর রচনার বিষয়ও ঐ এক কথা। কিন্তু সে কথা তাঁর হাতে হয়েছে রায়তের কথা।
২.
বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখ থেকে সবুজ পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় নানা বিষয়ে যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন তাদের রচনাকাল তখন থেকে মোটামুটি কুড়ি-পঁচিশ বছর। এ সময়ের পূর্বে তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্প। যদিও বাংলা গদ্যরচনায় সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষার যে যুদ্ধে চলিত ভাষার পক্ষের নেতা হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর বাংলাদেশে সব চেয়ে বেশি পরিচয়, তার কয়েকটি প্রবন্ধ এ সময়ের পূর্বে লেখা। কথায় কথা এ সময়ের অনেক পুর্বে ১৩০৯ সালের ভারতীতে প্রকাশ হয়; বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা’ ও ‘সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা’ এর অনতিকাল পূর্বে ১৩১৯ সালের শেষের দিকে ভারতীতে প্রকাশ হয়।
এর সমকালে ও অনতিপূর্বকালে দুইজনের লেখা প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলির মূল্য ও বিশেষত্ব হৃদয়ংগম হয়। সে দুইজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দ-বিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির বাগবৈভব। বিচারে যুক্তির মধ্যে হঠাৎ এল উপমা। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ান্তরের স্পর্শে অদ্ভুত ঐক্যের আলোর চমক পথ আলো করে দিল। প্রতিপক্ষের মনে হল এ অন্যায়। লড়াই চলছিল লাঠিতে লাঠিতে, তার মধ্যে তলোয়ারের ধার ও দীপ্তি আনা। ভাষা ও প্রকাশকে অনুদবেজিত রেখে শ্রোতার মনে আবেগ-সঞ্চারের যে কৌশল মহাকবির আয়ত্ত তার দোলা এসব প্রবন্ধে লেগেছে। বিষয়ভেদে সে দোল মন প্রকাশ্যে উপভোগ করছে, বিষয়ভেদে সে দোল মৃদুর চেয়েও মৃদু। বুদ্ধি ভাবে যা কিছু আয়োজন তাকে চলার পথে দ্রুত এগিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু অজ্ঞাতে পায়ে লেগেছে ছন্দের দোল। মহাকবির গদ্য, সুতরাং ভুলেও কোথাও পদ্যগন্ধী নয়। ভাষাপ্রয়োগের কলাকৌশল রয়েছে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু ব্যক্ত হয়েছে, এমন, গদ্যে যা গল্পলেখকের অসাধ্য। এ রকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ। যেমন দুর্লভ মহাকবির আবির্ভাব। আর তার চেয়েও খুলভ মহাকবির একরচনায় প্রেরণা। এ রচনা নানা শ্রেণীর প্রবন্ধের এক শ্রেণী নয়। এ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। পাগল ছাড়া এর অনুকরণের কথা কোনো লোক কল্পনা করে না।
আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সেকালের বেসরকারি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ছাত্রদের পদার্থবিজ্ঞানের ক খ পড়াতেন। সেই প্রাথমিক বিজ্ঞান পড়াতে পরীক্ষা দেখাবার জন্য যে সামান্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তারও বালাই ছিল না। সেসবের জায়গায় ছিল কালো বোর্ড আর সাদা চক। বিজ্ঞানের এই প্রাইমারি বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয় রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সর্ববিজ্ঞানবিদ্যার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। কিন্তু মহাপণ্ডিত বললে তার পরিচয় হয় না। বহু বিজ্ঞানের শিকড় থেকে ফুলফল পর্যন্ত সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানমাত্র নয়, সেসব বিজ্ঞানের গতি ও প্রকৃতিতে তার অন্ত ষ্টি ছিল অসাধারণ। উনবিংশ। শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানের পরিণতি, এবং সে শতাব্দীর শেষ দিকে তার নবপর্যায়ের সূচনার তথ্য ও তত্ত্বে তাঁর মন ভরে ছিল। সে জ্ঞান ও চিন্তার অল্প কিছু পরিচয় তিনি দিয়েছেন তার প্রথম দিকের নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে। আজ যেসব বাঙালি বিজ্ঞানী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও নববিজ্ঞানের চমৎকার পরিচয় দিচ্ছেন রামেন্দ্রসুন্দর তাদের গুরু। তাঁর সর্বজ্ঞানরসিক অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞানেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারে নি। বেদবিদ্যা ও বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন থেকে আরম্ভ করে মহাভারত ও মহাজন-চরিতকথার মধ্য দিয়ে বাংলার মেয়েলি ছড়া পর্যন্ত সে মনের স্বচ্ছন্দ গতি। ইংরেজ সমালোচক যে মনকে বলেছেন ‘বাদশাহী হীরা। জ্ঞানের আলো পড়লে শতমুখ থেকে কিরণ ঠিকরে আসে। রামেন্দ্রসুন্দরের শেষের দিকের প্রবন্ধগুলি তার এই বহুমুখী জ্ঞান ও চিন্তার পরিচয়। তাঁর বিশাল জ্ঞান ছিল তার মনের লীলাক্ষেত্র, তাকে বহন করতে হত না। তার লেখা প্রবন্ধ তার মনের প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তিনি বলেছেন অতি সহজে; তার পরিধির কথা ভাবলে তবে মনে বিস্ময় আসে। তার গভীর চিন্তা পাঠকের মনে চিন্তা আনে কিন্তু তার প্রকাশ গম্ভীর নয়। ভাষা অবলীলায় ভাবকে প্রকাশ করছে, কিন্তু তার গতি লঘু নয়। পদক্ষেপে মহার্ঘ শালীনতা। গভীর জ্ঞান ও চিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা। কিন্তু তার মধ্যে দেখা দিয়েছে অনাবিল হাসি। জ্ঞানীর বিমুক্ত মনের পরিচয়।
৩.
গৌতম বুদ্ধ আর্য ছিলেন, না, প্রত্যন্তবাসী আর্যেতর জাতির বংশধর, এ তর্ক প্রাচীন। এথনলজির প্রমাণে এর মীমাংসার কথায় প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—
“একদল আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, শাক্যসাত্বতাদি কুল আর্যবংশীয় নয়। কিন্তু এ মত যে সত্য তার কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। এ স্থলে এখনলজি নামক উপবিজ্ঞানের আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবে এইটুকু বলে রাখা দরকার যে, এথনলজিস্টদের হাত এখন আমাদের মাথা থেকে নেমে নাকের উপর এসে পড়েছে, সম্ভবতঃ পরে দাঁতে গিয়ে ঠেকবে। যারা মস্তকের পরিমাণ থেকে মানবের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীনত্ব নির্ণয় করতেন তাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ যে স্বল্প ছিল এ সত্য এথনলজিস্টরাই প্রমাণ করেছেন। এখন এদের বিজ্ঞানের প্রাণ নাসিকাগত হয়েছে। কিন্তু সে প্রাণ যতদিন না ওষ্ঠাগত হয় ততদিন এঁরা শাক্যসিংহের জাতি নির্ণয় করতে পারবেন না। কেননা বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত হয়েছে, নাসিকা হয় নি।” (‘আর্যধর্মের সহিত বাহ্যধর্মের যোগাযোগ’। সবুজ পত্র, ১৩২২ মাঘ)
অনুমান করা কঠিন নয় রবীন্দ্রনাথ যদি এ আলোচনা করতেন কৌতুকের শুভ্ৰহাস্যে ও দুটি-একটি উপমার বিস্ময়ের চমকে একটি রসবস্তু গড়ে উঠত। রামেন্দ্রসুন্দরের হাতের বিজ্ঞানবুদ্ধির তীক্ষ্ণ আলোতে এ অপবিজ্ঞানের সমস্ত ফাঁক প্রকট হত। প্রমথ চৌধুরী বিজ্ঞানের চর্মে ঢাকা অজ্ঞানের বুকে সোজাসুজি ছুরি বসিয়েছেন। সে ছুরির ধার ও ঔজ্জ্বল্য চোখে ধাঁধা লাগায়। কিন্তু সে ছুরি যে খুন করার ছুরি তাতে সন্দেহ থাকে না। এই অল্প কয়েক লাইন লেখার মধ্যে নানা জ্ঞানের ইঙ্গিত ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। যে মারাত্মক ব্যঙ্গ এর লক্ষ্য তাতে ভার ও ধার জোগানোই এদের কাজ।
প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধের অনেকগুলি এই রকম বিতর্কমূলক। কোনো প্রাচীন কি নবীন প্রচলিত ও প্রচারিত মতকে পরীক্ষা করে প্রায়ই তার উচ্ছেদ করা এদের লক্ষ্য। এ পরীক্ষায় যুক্তি ও তর্কের অনেক বিচার, দেশি ও বিদেশি তথ্য ও তত্ত্বের বহু আলোচনা। সে বিচার ও আলোচনার সামর্থ্য অল্প লেখকেরই থাকে। তার মূলে আছে অসামান্য ধীশক্তির বহু বছরের নানা জ্ঞান ও চিন্তার অনন্যমনা চর্চা। কিন্তু পাঠকের মনে এসব প্রবন্ধের প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ এ বিচার ও আলোচনার বিষয়বস্তুর নয়। বিচার ও আলোচনায় প্রবন্ধ কোথায় পৌঁছল সে মীমাংসারও নয়। যা প্রথম থেকে পাঠকের মনকে সজাগ ও মুগ্ধ রাখে সে হচ্ছে বিচার ও আলোচনার প্রকাশের ভঙ্গি।
এইসকল প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী যে রচনারীতি এনেছেন বাংলা সাহিত্যে তা নূতন। যেসব প্রবন্ধ বিতর্কমূলক নয় তারও রচনারীতি নূতন। বিষয় বৈচিত্র্যের অবধি নেই। ভাষা সাহিত্য, শিক্ষা সভ্যতা, প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস, সমাজ পলিটিক্স, চিরন্তন ও সাময়িক সকলের সেখানে স্থান। নানা জ্ঞান ও বিদ্যার অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ করেছেন যেন সহজে ঘরোয়া কথায়। যা প্রাচীন, সুতরাং নমস্য ও তর্কাতীত, বর্তমানের আলো ফেলে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। যা আধুনিক ও সাময়িক, অতিপ্রাচীনের মধ্যে তার ছবি আবিষ্কার করে মানুষের মন ও চরিত্রের মূল ঐক্য দেখিয়েছেন। আর, সকল আলোচনাকে অনুস্ত করে আছে এক দীপ্তিমান রসিকতার সুতীক্ষ্ণ সরসতা। পদবিন্যাসমাত্র যা মনকে অপহরণ করে। লেখকের মনের গড়ন-ভঙ্গি ছাড়াও যে এ রসিকতার মূলে আছে জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও বহুজ্ঞানচর্চায় শাণিত বুদ্ধি, পাঠকের সে কথা প্রথমে মনে হয় না।
প্রবন্ধগুলি যখন সবুজ পত্রে প্রকাশ হচ্ছিল, তাদের শব্দচয়ন ও শব্দগ্রন্থনের কৌশল, সংহত প্রকাশের পরিপাট্য পাঠকের মনকে যে সবচেয়ে দখল করেছিল তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। বলার ভঙ্গি বলার বিষয়কে মনে ছাপিয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে অংশটা প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভার একান্ত নিজস্ব তা ছাড়া তাঁর রচনারীতি বাংলা গদ্যরচনা, প্রবন্ধ ও সমধর্মী রচনাকে বহুল প্রভাবিত করেছে, লেখকদের জ্ঞানে ও অজ্ঞাতে। সাধু বনাম চলিত ভাষার তর্কে প্রমথ চৌধুরীর জয়ের চিহ্ন যেমন আজ বাংলা গদ্যরচনার সারা শরীরে, তেমনি তার রচনারীতির প্রভাব বাংলা গদ্যে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাক্-প্রমথ যুগের তুলনায় আজকের বাংলা গদ্য অনেক সংহত, তার গতি অনাড়ষ্ট, জটিলকে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের প্রসাদগুণ তার অনেক বেশি। এর মূলে প্রথম চৌধুরীর আদর্শের প্রভাব অনেকখানি। বাংলা গদ্যের ভাষা ও রচনারীতিতে তিনি যে পরিবর্তন। এনেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার বড় দান বলে তা স্বীকৃত হবে। কিন্তু তার বলার ভঙ্গিতে তার বলার বিষয় যদি চাপা পড়ে তা হবে দেশের দুর্ভাগ্য। এই ঋজু কঠিন তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে তিনি যা বলেছেন তার প্রধান কথা হচ্ছে মন ও সাহিত্যের মুক্তির কথা। সে কথা বলার প্রয়োজন চিরকাল থাকবে। এবং আজকের দিনে তার প্রয়োজন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি।
একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আজ আমরা যাকে বলছি ‘প্রগতিসাহিত্য’ বা ‘সমাজসচেতন সাহিত্য’ তার তর্ক খুব প্রখর হয়ে উঠেছে, ঐতিহাসিক কারণে। কিন্তু সবুজ পত্র যখন প্রথম প্রকাশ হচ্ছে সে তর্কের তখন অপ্রতুল ছিল না। মানুষের সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন; তার শ্রেণীভেদের, তার ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার, তার রাষ্ট্রশক্তির মূল উৎসের। এ আলোচনা তখন বেশ চলেছে; কারণ সময়টা প্রথম মহাযুদ্ধের উদ্যোগ ও ভীষ্ম–পর্ব। এ আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর মন ছিল মোটের উপর এই পরিবর্তনের পক্ষে। কিন্তু যখন দাবি উঠল যে, সাহিত্যের কাজ এই পরিবর্তনের পথকে সুগম করা, সাহিত্যিককে হতে হবে এই পথ তৈরির ইনজিনিয়ার তখন তিনি সাহিত্যের মূল প্রকৃতির কথাটি বললেন পরিস্কার করে ‘সবুজ পত্রের মুখপত্রে’— ওঁ প্ৰাণায় স্বাহা বলে যার আরম্ভ। একটা অংশ তুলে দিচ্ছি।
“…এ কথা সত্য যে মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতেহাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনো কথায় চিড়ে ভেজে না, কিন্তু কোন-কোনো কথায় মন ভেজে; এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের শক্তি অপরিসীম। তাই আমরা কথায় মরি কথায় বাঁচি। মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কি না জানি নে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। মানুষমাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র, মন বলে ভুল করিনিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানি নে কেননা জানি নে। সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।”
আজকের দিনে এর টীকায় বলা প্রয়োজন যে, ঘুমপাড়ানি গান শুধু মাঠাকুরমার মুখের প্রাচীন ছড়া নয়, যা শুনে শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ে। অতিনবীন সব ছড়া আছে যার সুরে অনেক বয়স্ক শিশুর মনের একদিক ছাড়া আর সব দিক ঘুমে অচেতন হয়। সাহিত্যের এক ফল সমস্ত মনকে জাগরূক করা। বিশেষ কাজের জন্য যাকে postulate স্বীকার করতে হয়, তা যে জ্ঞানের axiom নয় সে সম্বন্ধে মনকে সজাগ রাখা।
বস্তুতন্ত্র বস্তু কি’ প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী আবার লিখেছেন—
“সাহিত্যকে কোনো-একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ করে তুললে তাকে সংকীর্ণ করে ফেলা অনিবার্য। আমরা সামাজিক জীব, অতএব নূতন-পুরাতনের যুদ্ধেতে একপক্ষে-না-একপক্ষে আমাদের যোগ দিতেই হবে, কিন্তু আমাদের সমগ্র মনটিকে যদি আমরা এই যুদ্ধে নিয়োজিত করি তাহলে আমরা সনাতনের জ্ঞান হারাই। যা কোনো-একটি বিশেষ যুগের নয়, কিন্তু সকল যুগেরই হয় সত্য নয় সমস্যা, তাই হচ্ছে মানবমনের পক্ষে চিরপুরাতন ও চিরনূতন, এক কথায় সনাতন। এই সনাতনকে যদি রাধাকুমুদবাবু নিত্যবস্তু বলেন, তাহলে সাহিত্যের যে নিত্যবস্তু আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না; কিন্তু ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিকেরা তা অগ্রাহ্য করবেন। একান্ত বিষয়গত সাহিত্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার ইচ্ছা থেকেই ‘art for art মতের উৎপত্তি হয়েছে। কাব্য বল, ধর্ম বল, দর্শন বল, এসকল হচ্ছে বিষয়ে নির্লিপ্ত মনের ধর্ম। এই সত্য উপেক্ষা করার দরুন ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে।”
কিছু বিচিত্র নয় যে, যেখানে ‘সমাজসচেতন’ ‘প্রগতি’-সাহিত্যের আজ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সেখানেই তার উপদ্রবের পাল্টা দেখা দেবে ‘art for art সাহিত্য ও সাহিত্য-বিচার, রাষ্ট্রের চাপ যখন একটু আলগা হবে।
প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি বহু জায়গায় ছড়ানো রয়েছে; অনেক পাঠকেরই দুষ্প্রাপ্য। তার পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশ হচ্ছে এই প্রবন্ধ সংগ্রহে। এই পুনঃপ্রকাশে পাঠকের সঙ্গে প্রবন্ধগুলির নূতন পরিচয় হবে। নানা কষ্টিপাথরের বিচারে প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের বড় সম্পদ। প্রবন্ধগুলিতে মনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আহ্বান, উপদেশে ও আচরণে। প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের অন্ধতা থেকে মুক্তি, অর্থহীন বন্ধন থেকে মুক্তি। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির মনে এই মুক্তির বাণীর প্রতিষ্ঠা হোক।
অতুলচন্দ্র গুপ্ত
১৩৫৯ শ্রাবণ