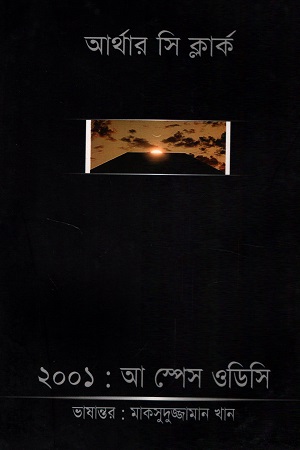- বইয়ের নামঃ ২০০১ : আ স্পেস ওডিসি
- লেখকের নামঃ আর্থার সি ক্লার্ক
- প্রকাশনাঃ বুক ক্লাব
- বিভাগসমূহঃ অনুবাদ বই, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী
২০০১ : আ স্পেস ওডিসি
০. প্রারম্ভ কথন
২০০১ : আ স্পেস ওডিসি – আর্থার সি ক্লার্ক
ভাষান্তর : মাকসুদুজ্জামান খান
[ষাটের দশকে ব্যতিক্রমী চিত্র পরিচালক স্ট্যানলি কুবরিক হঠাৎ ভাবলেন, প্রকৃত সায়েন্স ফিকশন চাই। সর্বব্যাপী, সর্বদৃষ্টির এক সায়েন্স ফিকশন বানাতে চাইলেন যাতে বিজ্ঞান আসবে পুরোপুরি যুক্তির কাঁধে ভর করে। স্নায়ুক্ষয়ী কাহিনী আসবে বিজ্ঞানের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে। স্যাটেলাইটের জনক, মহাকাশ অভিযানের ধারাভাষ্যকার কল্পবিজ্ঞানী আর্থার সি ক্লার্ক তাঁকে যে কাহিনী দিলেন তা দিয়ে সৃষ্টি হল ‘২০০১: আ স্পেস ওডিসি’।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্র। কিন্তু ক্লার্কের মনে হল, কাহিনী পূর্ণ হয়নি। তিনি একই নামে আরো পরিস্কার করে গুছিয়ে লিখলেন এই উপন্যাস। উনিশশ আটষট্টিতে। মহাকাশ অভিযান নিয়ে সারা পৃথিবীর সব সায়েন্স ফিকশনের আদর্শ।
এল অনেক তত্ত্ব। তারপর এর প্রভাব যে কোথায় পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর প্রতিটি মহাকাশ অভিযানের সায়েন্স ফিকশনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে ক্লার্কের মহাকাশ মহাকাব্য। ইসরায়েল তার মানবীয় কম্পিউটারের নাম দেয় তার দেয়া ‘হাল’ নামানুসারে, আমেরিকার নাসা আজো ‘ওডিসি’ নামে মিশন চালায়! ‘ওডিসি’ অনুবাদ হয় আটত্রিশটি ভাষায়, এ সিরিজের শেষ বইয়ের জন্য ক্লার্ক পান সায়েন্স ফিকশনে রেকর্ড সম্মানী। চল্লিশ বছরে ক্লার্ক আরো চারটি উপন্যাস লিখলেন। সৃষ্টি হল পৃথিবীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সায়েন্স ফিকশন সিরিজ। মহাকাশ অভিযানের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।
ত্রিশ লাখ বছর আগে প্রাচীন ক্ষুধা-তৃষ্ণার জান্তবতা থেকে বন মানুষের দল চলা শুরু করে, শুরু হয় ওডিসি, এর শেষ দু হাজার এক সালে, পৃথিবী থেকে বিশ হাজার আলোক বর্ষ দূরের এক বিশাল, দানবাকার নক্ষত্রের গর্ভে। এ ক্লাসিক উপন্যাস না পড়লে যে কোনো বিজ্ঞান সচেতন পাঠকের সায়েন্স ফিকশনের স্বাদ অপূর্ণ থেকে যাবে। আর্থার সি. ক্লার্ক ১৯ মার্চ ২০০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]
.
অনুবাদক মাকসুদুজ্জামান খান বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ালেখা করছেন। তিনি আর্থার সি ক্লার্ক ও আইজাক আসিমভের বেশ কিছু লেখা ভাষান্তর করেছেন।
.
বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সায়েন্স ফিকশন লেখক আর্থার চালর্স ক্লার্ক। তিনিই স্যাটেলাইট বিজ্ঞানের জনক। ক্লার্কের অমর কীর্তি ‘২০০১ আ স্পেস ওডিসি’র কথা সায়েন্স ফিকশন পাঠকদের বলাটা এক ধরনের বাহুল্য। সেই চিরায়ত গ্রন্থের অমীমাংসিত রহস্য-পর্দা উন্মোচিত হয়েছে ‘২০১০ ওডিসি টু’তে কিন্তু সেটা শুধুই আগের পর্বের মানুষের শেষ পরিণতি নিয়ে টানা হেঁচড়া নয়। বরং এ খন্ডে তিনি সম্পূর্ণ নতুন, অনন্যসাধারণ আরো একটি পরিণতি রেখেছেন। এটা ২০০১ এর নক্ষত্র শিশুর চেয়ে কোনো অংশে কম ধাক্কা দেয় না পাঠকের মনে।
২০০০ সালের দিকে বিজ্ঞান প্রবেশ করে মহাকাশ যুগে। মানুষ প্রথমবারের মতো পৃথিবীর বাইরে ঘাটি করে। চাঁদের দেশে। আমেরিকান ঘাঁটির নাম ক্ল্যাভিয়াস বেস। সেখানে এক এলাকায় চুম্বক রেখা বারবার এলোমেলো হয়ে যায়।
বিজ্ঞানীরা চল্লিশ ফুট পাথুরে জমির নিচে খুঁড়ে বের করে কালো একটা বস্তু। ত্রিশ লাখ বছরের পুরনো। যত অনুবীক্ষণিক যন্ত্র দিয়েই দেখা হোক, দেখতে একই রকম। সূর্য ওঠার সাথে সাথে সেটা থেকে একটি রেডিও তরঙ্গ ভেসে যায় সৌর জগতের প্রান্তসীমায়। যেন চিৎকার করে বলছে, মানুষ যোগ্য হয়েছে, সে পৃথিবী থেকে চাদে এসে আমাকে খুঁড়ে বের করে আমার গায়ে সূর্যের আলো ফেলেছে… বৃহস্পতি-শনির দিকে পাঠানো হল ডিসকভারি স্পেসশিপ, সাথে মানবীয় কম্পিউটার-হাল। তারপরের সবটুকুই ইতিহাস। অবাক করা ইতিহাস।
ডিসকভারির অধিনায়ক ডেভিড বোম্যান এক অপার্থিব সত্যের মুখোমুখি হয়… এমন কালো বস্তু পৃথিবীতেও ছিল লক্ষ বছর আগে…দু দল বানর পানি নিয়ে ঝগড়া করে ফেরার সময় এর সামনে দাঁড়াত, দেখত ছুঁয়ে… আরাধ্য সত্যের সন্ধান পায় ডেভ বোম্যান। কিন্তু মানুষ তা জানতে পারে না।
মানুষ হারও মানে না। মানতে জানে না। তাই ২০১০ সালে তারা ডিসকভারির সেই ব্যর্থতার কথা মনে রেখেও লিওনভকে প্রস্তুত করার সাহস পায়। কিন্তু এবারের পরিণতিটা অন্যরকম।
.
পঁয়ত্রিশটি ভাষায় অনূদিত মহাকাশ উপন্যাস ওডিসি সিরিজ
২০০১: আ স্পেস ওডিসি
আর্থার সি ক্লাক
অনুবাদ : মাকসুদুজ্জামান খান
.
2001
A SPACE ODYSSEY
ARTHUR C. CLARKE
.
উৎসর্গ
সাত বছরের বন্ধুত্ব শেষে নাফিস আমাকে বলেছিল,
‘দোস, বন্ধু বললে মানুষ আমাদের বন্ধুত্বটা ঠিক বোঝে না।
এখন থেকে আমরা কাজিন।
কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করি,
ভাই হিসেবে পরিচয় দিয়েও গভীরতাটা বোঝানো দুষ্কর
আহমেদ নাফিস শাহরিয়ারকে
.
যঅনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতির সময় তার পাঠানো চিঠিতে
২২ আগস্ট, ১৯৯৪
প্রিয় আর্থার,
সরি, ফিল্মের কাজের চাপ আমাকে আপনার এই বিশেষ সম্মান পাওয়া দেখা থেকে বঞ্চিত করল। নয়তো আজ রাতে আমি অবশ্যই এখানে থাকতাম।
প্রত্যাশা অনুযায়ী আপনিই পৃথিবীর সবচে পরিচিত সায়েন্স ফিকশন লেখক। আপনি এক মানুষ হয়ে আমাদের ধুলোর পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের জগতে নিয়ে যাবার পথে যে কাজ করেছেন তা আর কোনো একক ব্যক্তিত্ব করতে পারেনি। এমন এক সময়ে নিয়ে যাবার কাজ করছেন যেখানে অচেনা বুদ্ধিমত্তার কাছে মানুষ হবে ঈশ্বর পিতা, বা গডফাদার।
অন্যক্ষেত্রে, যখন এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে, ইউনিভার্সের অসীম পথে পরিভ্রমণ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে, তখন তাদের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়বে, পড়বেই। তারাও শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করবে তার প্রতি যিনি তাদের অস্তিত্বের সবচে বড় এবং দূরদর্শী সমর্থক।
.
কিন্তু কে জানে, আগামীদিনের মানুষ আপনার সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবে কিনাঃ পৃথিবীতে আদৌ বুদ্ধিমত্তা আছে তো?
আপনার,
স্ট্যানলি
.
এই ক’দিন আগেও আমি স্বপ্ন দেখছিলাম তাকে নিয়ে। যেমন ছিলেন ১৯৬৪ সনে, তেমনি। প্রশ্ন করলেন, ‘যাক, এখন কী করণীয়?’ তো, যদি এরপর বলে আসলেই কিছু থেকে থাকে, সেখানে ব্রায়ান এলডিসের চমৎকার ছোটগল্প ‘সুপারটয় সারা গ্রীষ্ম জুড়ে ভাল রয়’ অনুসরণে তিনি ‘এ আই’ নামে যে ছায়াছবিটা গড়তে চান এবং নানা ঝুট-ঝামেলায় কুলিয়ে উঠতে পারেননি সেসব কথা মনে পড়ে।
আমার এক জীবনে সবচে গভীর দুঃখের মধ্যে একটা, ২০০১ সাল একদিন আসবে, সেদিন আমার পাশে মহান চলচ্চিত্রকার স্ট্যানলি কুবরিক থাকবেন না।
আর্থার সি ক্লার্ক
১৬-০৪-১৯৯৯
.
স্ট্যানলির স্মৃতির প্রতি
সামনের ভূমিকাটা লেখার মাত্র সপ্তাহদুয়েক পরেই নিথর করে দেয়া অপ্রত্যাশিত এক খবর পেলাম। স্ট্যানলি কুবরিক সত্তর বছর বয়েসে মারা গেছেন। দু-হাজার এক সালে আমাদের চলচ্চিত্রটার এক নতুন রূপ মুক্তি দেয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর; তার সাথে অংশীদারিত্বের দিন ফুরিয়ে যাওয়াতে আমার অন্তরের অন্তস্থল সত্যি সত্যি ব্যথায় ভরে উঠছে।
২০০১ শেষ করার পর তিন দশকে আমাদের খুব কমই দেখা হয়েছিল। কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল অটুট। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় বি বি সি-র দিস ইজ ইউর লাইফ অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতির সময় তাঁর পাঠানো চিঠিতে:
২২ আগস্ট, ১৯৯৪
প্রিয় আর্থার,
সরি, ফিল্মের কাজের চাপ আমাকে আপনার এই বিশেষ সম্মান পাওয়া দেখা থেকে বঞ্চিত করল। নয়তো আজ রাতে আমি অবশ্যই এখানে থাকতাম।
প্রত্যাশা অনুযায়ী আপনিই পৃথিবীর সবচে পরিচিত সায়েন্স ফিকশন লেখক। আপনি এক মানুষ হয়ে আমাদের ধুলোর পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের জগতে নিয়ে যাবার পথে যে কাজ করেছেন তা আর। কোনো একক ব্যক্তিত্ব করতে পারেনি। এমন এক সময়ে নিয়ে যাবার কাজ করছেন যেখানে অচেনা বুদ্ধিমত্তার কাছে মানুষ হবে ঈশ্বর পিতা, বা গডফাদার।
অন্যক্ষেত্রে, যখন এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে, ইউনিভার্সের অসীম পথে পরিভ্রমণ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে, তখন তাদের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়বে, পড়বেই। তারাও শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করবে তার প্রতি যিনি তাদের অস্তিত্বের সবচে বড় এবং দূরদর্শী সমর্থক।
কিন্তু কে জানে, আগামীদিনের মানুষ আপনার সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবে কিনাঃ পৃথিবীতে আদৌ বুদ্ধিমত্তা আছে তো?
আপনার,
স্ট্যানলি
.
এই কদিন আগেও আমি স্বপ্ন দেখছিলাম তাকে নিয়ে। যেমন ছিলেন ১৯৬৪ সনে, তেমনি। প্রশ্ন করলেন, ‘যাক, এখন কী করণীয়?’ তো, যদি এরপর বলে আসলেই কিছু থেকে থাকে, সেখানে ব্রায়ান এ্যলডিসের চমৎকার ছোটগল্প ‘সুপারটয় সারা গ্রীষ্ম জুড়ে ভাল রয়’ অনুসরণে তিনি ‘এ আই’ নামে যে ছায়াছবিটা গড়তে চান এবং নানা ঝুট-ঝামেলায় কুলিয়ে উঠতে পারেননি সেসব কথা মনে পড়ে।
আমার এক জীবনে সবচে গভীর দুঃখের মধ্যে একটা, ২০০১ সাল একদিন আসবে, সেদিন আমার পাশে মহান চলচ্চিত্রকার স্ট্যানলি কুবরিক থাকবেন না।
আর্থার সি ক্লার্ক
১৬-০৪-১৯৯৯
সহস্রাব্দ সংস্করণের কথা
আজ পঁয়ত্রিশ বছর হল, একদিন স্ট্যানলি কুবরিক তার সেই ‘ভালো সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্র’ খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। আসল সত্যি বলতে গেলে, বর্তমানের চোখে ১৯৬৪ সালটা যেন অন্য যুগের অধীনে বাস করে। সেই তখন, মাত্র হাতেগোনা দু-চারজন নভোচর মহাকাশে ঢু মেরেছে এবং মহিলাদের আরো দৈন্যদশা, মাত্র একজন। তখন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ঘোষণা করলেন, দশক পেরুনোর আগেই মানুষ চাঁদের বুকে পা রাখবে। এখন আমি বাজি ধরতে পারি, খুব বেশি লোক সে কথা বিশ্বাস করেনি সেদিন।
আরো হতাশ করা ব্যাপার হল, মহাকাশে আমাদের চিরসাথী, সবচে কাছের আত্মীয়ের ব্যাপারে আক্ষরিক অর্থে কোনো প্রামাণ্য ধারণা ছিল না আমাদের মনে। এমনকি চাঁদের বুকে প্রথম ভোব নামার সময় কোনো ধুলার সাগরে যে ডুবে যাবে না তাও নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনি।
ব্যাপারটা খোলাসা করার জন্য উনিশশো একাত্তরে, যখন আমার মাথা কিছুটা পরিষ্কার ছিল তখন লেখা নন-ফিকশন (আংশিক) টার কথা মনে করিয়ে দিতে দিন। দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ডস অফ ২০০১-এ লিখেছিলাম:
চৌষট্টির বসন্তে… চান্দ্র অবতরণ মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দূরের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে আমরা জানতাম, এ অপ্রতিরোধ্য। আর আবেগের দিক দিয়ে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি… গ্রিসাম আর ইয়ংয়ের দ্বি-মানব যান আরো এক বছর পরও হালে পানি পায়নি। তখনো চাঁদের বুকের গঠন নিয়ে যুক্তি-পাল্টা যুক্তির ঝড় বইছে… যদিও নাসা আমাদের পুরো ছায়াছবির বাজেট (কোটি ডলারের উপরে) প্রতিদিন খরচ করছে, দেখেশুনে স্পেস অভিযানকে পাহাড় ডিঙানোর চেয়ে লাখ গুণ কঠিন বলেই মনে হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল স্থির, মানুষ চাঁদের বুকে হাঁটাহাঁটি করার সময়ও এই ছায়াছবিটা সমান জনপ্রিয়তা রাখবে।
সুতরাং, আমাদের কাহিনীটা লিখতে অনেক ঘাম ঝরাতে হল। এমন কিছু লিখতে হবে যেটা বাস্তবের নির্যাসে সিক্ত থাকবে না শুধু, বরং তাই হবে বাস্তব। আবার সেই বাস্তবটা পরের ক’বছরের মধ্যে হলে চলবে না।
আমাদের প্রথম টাইটেলটা ছিল: কীভাবে সৌরজগৎ বিজিত হল। কিন্তু স্ট্যানলি সোজা কথায় একটা অভিযানের বাইরের রূপ বলে দিতে চাননি। তাছাড়া তিনি আমাকে সারাক্ষণ যে কথাটা বলে মজা পেতেন, তা হল, ‘আমি পৌরাণিকতার ঘ্রাণ নিতে ভালবাসি…’
কিন্তু, আজ ২০০১ এই একটু সামনে। হয়তো সে কারণেই ছায়াছবিটা সাধারণ্যে এক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। আমার বড় সন্দেহ হয়, তার সবচে বড় স্বপ্নগুলোতেও স্ট্যানলি কখনো কি ভেবেছিলেন যে একটা সুপার বল খেলার ঘোষক যখন ত্যালত্যালে কণ্ঠে বলবে, ‘ইট ওয়াজ এ বাগ, ডেভ। তখন টিভির সামনে বসা দশ কোটি আমেরিকানই সাথে সাথে চিনতে পারবে ঠিক কে (বা কোন জিনিসটা…) কাকে কখন এ কথাটা বলেছিল।
আরো একটা ব্যাপার, আই বি এম তার এক মেশিনের নামকরণ যখন সেই পুরনো হাল এর সাথে মিলিয়ে রাখে তখনো স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হতে হয়। যোড়শ অধ্যায়ে পুরো নামটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
যদি পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখতে চান তো আপনাদের সেই চমৎকার ভয়েজার ক্রাইটেরিয়ন ডিস্ক দেখার কথা বলব। পুরো মুভিটাতো আছেই, সেই সাথে তৈরির সময়ের ব্যাপারগুলোও দেয়া আছে সেখানে। ছবি শু্যট করার সময়ে বাড়তি দৃশ্য সহ বিজ্ঞানী, শিল্পী, টেকনিশিয়ানদের সাক্ষাৎকারও আছে। সেখানে একজন মোটামুটি তরুণ আর্থার সি ক্লার্কের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যও আছে। চাঁদের সেই কনফারেন্স রুমে নেয়া হয়, চারপাশে মুভিতে ব্যবহার করা এমন সব জিনিস ছিল কিছুদিন পরেই যেগুলো চাঁদের বুকে বিশ্রাম করার সুযোগ পায়। ব্যাপারটা শেষ হয় আরো বিরক্তিকর কিছু দৃশ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে আসা অ্যাপোলো, স্কাইল্যাব সহ অন্যান্য শাটলের সাথে স্ট্যানলির স্বপ্নের কাজের মিল দেখানো হয় পাশাপাশি তুলনা করে।
আমার কাছে ব্যাপারটা তেমন অবাক করা নয়, চলচ্চিত্রের সাথে বইটির মিল নেই, এ দুয়ের সাথে বাস্তবতার তেমন মিল নেই এবং বাস্তবতার সাথে পাল্লা দিয়ে আরো হাজারটা চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারি তৈরি হচ্ছে। তাই আমি একেবারে শুরুতে ফিরে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা কোত্থেকে শুরু হল তা আরেকবার মনে করতে চাই।
১৯৬৪’র এপ্রিলে আমি সিলন ছেড়ে গেলাম। সেকালে এ নামেই ডাকা হত জায়গাটাকে। তারপর নিউইয়র্কে সময় ও জীবদ্দশা নিয়ে লেখা ম্যান এন্ড স্পেস বইটার এডিটিং শেষ করার কাজে ঝুঁকেছিলাম। সেখানকার একটা কথা তুলে দেয়ার লোভ সামলে উঠতে পারছি না।
.
সিলনের ভূ-স্বর্গে বেশ ক’বছর কাটানোর পর আবার নিউইয়র্কে ফিরে আসাটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। আই আর টি’র মাত্র তিনটা স্টেশনে ঘুরে বেড়ানোও আমার জন্য মহা ব্যতিক্রম এবং ভালো একটা রিল্যাক্স। বিশেষত দিনগুলো যেখানে কাটত হাতির দলে, প্রবাল রিফে, নানা রঙের মৌসুমে ঘুরে বেরিয়ে ডুবে যাওয়া পুরনো দিনের জাহাজের সাঁতার কেটে হরদম দিন কেটে যেত। অন্যদিকে আজব চিৎকার, হাস্যোজ্জ্বল হাজার মুখ, রহস্যময় সম্পর্কের পথে ম্যানহাটানীয়দের একেবারে নিপাট ভদ্র ব্যবহার বিমোহিত করে মুগ্ধতার অন্য অংশকে; তেমি অবাক করে কোমল হুইসেল বাজাতে বাজাতে দিক-চিহ্নহীন সাবওয়ে স্টেশনে ছুটে চলা বজ্রগতির রেলগাড়িগুলোে, বাহারি বিজ্ঞাপন (কোনো কোনোটা আবার অপেশাদার আর্টিস্ট গুবলেট করে ফেলেছে, সেই কাঁচা হাতের কাজও মানিয়ে যাচ্ছে কেমন করে যেন) অযুত রঙে ঝকমক করছে কতশত ব্র্যান্ডের নাম নিয়ে-দ্য নিউইয়র্ক পোস্ট, লেভি’স ব্রেড, পাইল’স বিয়ার, আর মুখের ক্যান্সার উৎপাদনে মহা কার্যকর ডজনখানেক ব্র্যান্ডের কামড়া-কামড়ি। মজার ব্যাপার হল, একটা ব্যাপারে অভ্যস্ত হতে আপনার মিনিট পনের সময় লাগবে, ব্যস। এবং একই সময়ে সেটা মিলিয়ে যাবে মন-মগজ থেকে। (রিপোর্ট অন প্ল্যানেট থ্রি থেকে ‘সন অব ড. স্ট্রেঞ্জলাভ’)
.
ম্যান এন্ড স্পেসের উপর আমার কাজ ভালোভাবে এগুনোর সময়টায় সময় আর জীবন নিয়ে কাজের প্রতি ঈর্ষান্বিত এক সমালোচক বলেছিলেন, ‘এই জবানি দেয়ার অধিকার আপনার আছে? কোথায় সেটা?’
আমি মহিলার দিকে সর্বস্ব ভস্ম করে দেয়া একটা দৃষ্টি হেনে বললাম, ‘আপনি তার দিকেই চেয়ে আছেন।’
সুতরাং, স্ট্যানলির সাথে জোছনা উপভোগ করার মতো সময় আমার হাতে ছিল এবং বেশ ভালোভাবেই ছিল। তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ট্রেডার ভিক-এ। (তাদের উচিত জায়গাটাকে চিহ্নিত করে রাখা) স্ট্যানলি তখনো তার শেষ ছবি ড, স্ট্রেঞ্জলাভ নিয়ে সোয়াস্তির জাবর কাটছেন এবং আরো উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রজেক্টের ধারণা পাবার অপেক্ষায় দিন গুনছেন। তার লক্ষ্য আরো বড়, ইউনিভার্সে মানুষের অবস্থান নিয়ে কিছু একটা করে দেখানোর ইচ্ছা তাঁর। এমন কিছু করা যার ফলে পুরনো বা নতুন স্কুল শিক্ষকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।
স্ট্যানলি এমন এক লোক, যিনি যে কোনো বিষয় মাথায় আসার সাথে সাথে সেটাতেই একেবারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতেন। সকল কাজের মহাকাজি। ততদিনে বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক বেশ কয়েকটা লাইব্রেরি তিনি হজম করে বসে আছেন। এর মধ্যেই একটা সম্পদের স্বত্ব কজা করে নিয়েছেন যেটাকে বলা হয় ‘শ্যাডো অন দ্য সান। আমার মনে পড়ে, তিনি লেখাটা নিয়ে কিছু বলতে পারেননি এমনকি এর লেখকের নামও আমি জানতাম না। সম্ভবত লোকটা সায়েন্স ফিকশনে নবাগত। কিন্তু বেচারার ক্যারিয়ারের গুড়ে আমি বালি ছড়িয়ে দিলাম। কুবরিকেরও কানে কথাটা এসেছিল, ক্লার্ক অন্যের আইডিয়া ডেভলপে তেমন আগ্রহী নয়। (রামা টুর শেষদিকটা দেখুন, কদশক পরে ক্রেডলের সাথে একটা যোগসূত্র বের করা যায়। তারপর, ফয়সালা হল, আমরা একেবারে নতুন কিছু তুলে আনব।
এখন, মুভি গড়ার আগে স্ক্রিপ্ট চাই, স্ক্রিপ্ট পাবার আগে চাই একটা গল্প। যদিও কালস্রষ্টা কিছু পরিচালক শেষের দু বিষয়কে পুরো উড়িয়ে দেয়ার অনেক চেষ্টা করেছেন, তবু তাদের ছায়াছবি খুঁজে পেতে হলে আপনাকে আর্ট থিয়েটার চষে বেড়াতে হবে। হাতে সময় নেই। আমি স্ট্যানলির হাতে আমার ছোট লেখাগুলোর একটা ফর্দ ধরিয়ে দিলাম, তার মধ্যে ‘দ্য সেন্টিনেল’কে আমাদের দুজনেরই বেশ মনে ধরল; এর উপর একটা ভিত্তি দাঁড় করানো যায়।
উনিশশো আটচল্লিশের ক্রিসমাসে শক্তি বিস্ফোরণের মতো গল্পটা লেখা হয়, বিবিসি ছোটগল্প প্রতিযোগিতার জন্য। গল্পটা মেধা তালিকায় উঠে আসেনি। আমার সারাক্ষণ ভাবনা ছিল, কোনো গল্প উঠল! যাই হোক, আমার গল্পটা পরে অ্যাক্সপেডিশন টু আর্থ-এ জায়গা পায়। আমার ভাবনা ছিল, চাঁদে একটা ট্রিগার পুঁতে রাখা হবে মানব জাতির উত্থানের সংকেত পাঠানোর জন্য।
অনেকে বলে বেড়ায় ২০০১ আসলে দ্য সেন্টিনেলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এ দুয়ের মিল ততটুকুই যতটুকু মিল আছে ওক গাছের কাণ্ড আর ফলের মধ্যে। মুভিটা বানাতে আরো হাজারটা কাঁচামাল প্রয়োজন, দরকার সেগুলোর প্রক্রিয়াকরণ। ‘ভোরের প্রথম মোকাবিলা’ থেকেও আরো কিছু তথ্য এল। এটাও পরে অ্যাক্সপেডিশন টু আর্থ-এ যুক্ত হয়। সময় কম। সব চেঁছে ফেলে নতুন করে লেখার মতো পরিস্থিতি হাতে নেই। লেখাটা একটা মাত্র পর্যায়, তারপর আরো এমন ডজনখানেক পর্যায় পেরিয়ে মুভির কারবার শেষ করতে হবে। তাই আরো অন্য চারটা ছোটগল্প থেকে কিছু কিছু অংশ নিতে হয় আমাদের। কিন্তু চলচ্চিত্রটার এই ছ’ অংশ ছাড়া বাকী সব এক্কেবারে নতুন। আমি, স্ট্যানলির সাথে মাথা ঘামাঘামি করে নির্ভেজাল লোনলি সময় কাটিয়েছি মাসের পর মাস, পশ্চিম ২৩ তম স্ট্রিটের ২২২ নম্বরের বিখ্যাত হোটেল চেলসিয়াতে, রুম নাম্বার ১০০৮-এ।
বেশিরভাগ উপন্যাস লিখেছিলাম এখানে। এখানেই ব্যথাভরা ‘দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ডস অব ২০০১’ লিখতে হয়। কেন উপন্যাস লেখা, যেখানে তৈরি করতে চাচ্ছি একটা চলচ্চিত্র! প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা। কথাটা সত্যি, নভেলাইজেশন (আহা!) পরে হওয়ার একটা রীতি চালু আছে বেশ জোরদার পন্থায়। স্ট্যানলি ঘড়ির কাঁটা উল্টে দিতে চাইলেন, ব্যস।
কারণ, স্ক্রিনপ্লে’র ঝক্কি জগদ্বিখ্যাত। এত বেশি ডিটেইল হতে হয় যে এটা পড়তে ততটাই খাটনি যতটা হয় লিখতে। জন ফাউলস কথাটা বেশ সুন্দর বলেছিলেন, ‘উপন্যাস লেখা হল অকূল পাথারে সাঁতার দেয়া। আর স্ক্রিনপ্লে? চিত্রনাট্য লিখতে যাওয়া সুগার রিফাইনারির তরল চিনিতে দ্রুত এগুতে চাওয়ার নামান্তর।’
একঘেঁয়েমিতে আমার এলার্জির ব্যাপারটা ধরতে পেরে স্ট্যানলি তাই হয়তো প্রথমে একটা উপন্যাস গড়তে চাইলেন। এর উপর ভিত্তি করেই সাথে সাথে একটা সুন্দর পাণ্ডুলিপি তুলে আনা যাবে। সেই সাথে কিছু পয়সা।)
এবং শেষকালে স্ক্রিনপ্লে আর নভেল একই সাথে সমাপ্তির পথে এগোয়, একই সাথে দ্বিমুখী চাপে পড়ে। তারপর আমি ছবিটা দেখলাম, যেটা খুব কম লেখকই উপভোগ করেছে। (আমার মনে হয় এনজয়’ কথাটা বলা ঠিক হল না।) আর শেষে বদলে দিলাম কয়েকটা চ্যাপ্টার।
সকালে তাড়াহুড়ো করে যে কটা ঘটনার নাম লিখেছি তা থেকে আমাদের নাকে-মুখে খাওয়ার একটু নমুনা পাওয়া যেতে পারে।
.
মে আটাশ, উনিশশো চৌষট্টি, আমি স্ট্যানলিকে বললাম, ‘তারা মেশিন হলেই ভালো, যারা জীবদেহের গঠন নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করবে আমাদের মুভিটাতে। স্ট্যানলি গররাজি, নিমরাজি, পুরো রাজি….
জুন, দুই, গড়ে দৈনিক এক বা দু-হাজার শব্দ লিখছি। স্ট্যানলি বলছেন, আমরা এখানে একটা বেস্ট সেলার পেতে যাচ্ছি অচিরেই।
জুলাই, এগারো, প্লট নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে সারাক্ষণ ‘ক্যান্টর’স ট্রান্সফিনিট গ্রুপ নিয়ে বিতণ্ডায় মেতে থাকতে হল। আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে সে একজন গণিত-জিনিয়াস।
জুলাই, বারো। সব আছে, শুধু প্লটটা নেই।
জুলাই, ছাব্বিশ। স্ট্যানলির ছত্রিশতম জন্মদিন। তারপর গ্রামে গিয়ে একটা কার্ড পেলাম, লেখা, তুমি কী করে একটা জন্মদিন পালন কর যেখানে যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়াটা ফেটে যেতে পারে!’ ( ১৯৯৯ এর আপডেট: আশা করি সেসব কার্ড আরো পাব, প্রচুর পরিমাণে।)
সেপ্টেম্বর, আটাশ। স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন এক রোবট। বারবার বানানো হচ্ছে আমাকে। স্ট্যানলির কাছে আরো দু-অধ্যায় নিয়ে গেলাম, সাথে লেখা, ‘জো লেভিন এ কাজ তার লেখকদের জন্য করে না।’
অক্টোবর, সতের। স্ট্যানলি এমন একটা উপায় পেলেন যাতে এমন একটা রোবট বানানো সম্ভব হবে যেটা আমাদের হিরোদের ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের মতো মহানায়কে পরিণত হবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।
নভেম্বর আটাশ, আইজাক আসিমভকে ফোন করলাম। নিরামিষাশীর আমিষভোজীতে পরিণত হতে কী বায়োকেমিস্ট্রি দরকার তা জানতে।
ডিসেম্বর, দশ। স্ট্যানলি এইচ জি ওয়েলসের থিস টু কাম দেখে আমাকে বললেন যে তিনি জীবনে আর যাই করেন না কেন, আমার উপদেশানুযায়ী কোনো চলচ্চিত্র বানাবেন না।
ডিসেম্বর, চব্বিশ। ধীরলয়ে পাতা উল্টে যাচ্ছি, যাতে স্ট্যানলিকে একটা ক্রিসমাস উপহার হিসেবে দেয়া যায়।
.
এটুকু দেখে মনে হতে পারে আমাদের কাজের সমুদ্র শেষ হয়েছে। কিন্তু না। বিধি বাম। আসলে বইটার দু’তৃতীয়াংশ গেল মাত্র। কারণ, আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এরপর কী হতে যাচ্ছে। কিন্তু এম জি এম আর সিনেরোমা’র সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে এটুকুই যথেষ্ট। তো, বেঁধে ফেললেন স্ট্যানলি। প্রাথমিক নামটা ছিল, জার্নি বিয়োন্ড দ্য স্টার্স’। (অন্য দিকে, কীভাবে সৌরজগৎ বিজিত হয়েছিল তা মোটেও বেখাপ্পা নয়, বরং পরিপূরক। কিন্তু আপনি আমাকে ডাকবেন না, তাহলে আমিও আপনাকে বিরক্ত করব না।)
উনিশশো পঁয়ষট্টির হিসাবে স্ট্যানলি ভবিষ্যৎ কল্পনায় অসম্ভব জটিলতা আনছিলেন। ব্যাপারটা আরো গুবলেট হয়ে যায় যখন সিদ্ধান্ত হল যে শু্যটিং হবে ইংল্যান্ডে যেখানে তিনি এখনো নিউইয়র্ক থেকে পাততাড়ি গোটাননি। গোদের উপর বিষফোঁড়া, কোনোমতেই তার আকাশ ভ্রমণ চলবে না।
সমালোচনা করছি না কিন্তু, পাইলটের লাইসেন্স নেয়ার সময়ও স্ট্যানলির অবস্থা বেশি সুবিধাজনক ছিল বলে মনে হয় না। ঠিক যে কারণে ১৯৫৬ সালে আমি সিডনিতে ড্রাইভিং টেস্টে পাশ করার পর আজো হুইল হাতে নিইনি। আমিও জীবনকে বড্ড ভালোবাসি।
স্ট্যানলি ছায়াছবিটা শেষ করছেন, আমি টানাটানি করছি উপন্যাস ভার্সনটা নিয়ে, শেষভাগ নিয়ে যুদ্ধ করছি। কিন্তু ছাপার বেলায় তার সাথে কথা বলে নেয়ার সময় নেই। তিনি কাজে নাক পর্যন্ত ডুবে আছেন দিনরাত। কসম কেটেছিলেন, বই প্রকাশের আগে মুভিটা মুক্তি দেয়ার জন্য হন্যে হয়ে যাননি। কিন্তু আমি হন্যে হয়ে গিয়েছিলাম আটষট্টিতে।
এর জটিল গোলকধাঁধা দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই, মুভি থেকে বই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন হবেই। স্ট্যানলি সিদ্ধান্ত নিলেন, ডিসকভারি শিপটা বৃহস্পতিতে নামবে, যেখানে মূল উপন্যাসে সেটা শনির অতিথি, বৃহস্পতির গ্র্যাভিটিশনাল ফোর্সকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায়।
গতিবৃদ্ধির এই পথ ব্যবহার করেছিল ভয়েজার স্পেসক্রাফট; এগার বছর পর।
শনির বদলে কেন বৃহস্পতি? অন্তত তাতে করে কাহিনীর ধারা আরেকটু সহজ হয়, ব্যস। কিন্তু তারচে বড় কারণ হল, স্পেশাল ইফেক্ট ডিপার্টমেন্ট এমন শনি তৈরি করতে পারেনি যেটা স্ট্যানলিকে খুশি করতে পারবে। তাতে ভালই হল, কারণ ভয়েজার মিশনে শনির বলয়কে কল্পনার চেয়েও জটিল হিসেবে উপস্থাপিত করেছিল পরে; ফলে সেই শনি উপস্থাপিত হলে এতদিনে ছবিটা রদ্দি হয়ে যেত।
জুলাই আটষট্টিতে উপন্যাসটা মুক্তি পাবার এক যুগেরও পরে আমার সেই ওডিসি নিয়ে দ্বিতীয় উপন্যাস লেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। সব তো আর আমাদের ইচ্ছানুযায়ী চলে না, ভয়েজারের সেই দারুণ অভিযান আমাকে আরো খুশি করল। আমি আর স্ট্যানলি যে জায়গা নিয়ে স্বপ্নের বেসাতি করেছিলাম সাঁৎ করে সেটাই বাস্তবের দোরগোড়ায় কড়া নাড়তে শুরু করল। বদলে গেল আমার মন-মগজ। কে জমাট পানিতে মোড়া উপগ্রহ আশা করেছিল, কে ভেবেছিল সালফারের অগ্নিগিরির শত কিলোমিটার উঁচু আগুন-বর্ষণ রূপে দোজখ লুকিয়ে আছে বৃহস্পতির আরেক উপগ্রহে।
আজ, সায়েন্স ফিকশন আরো বিশ্বাস্য হতে পারে সত্যিকার সায়েন্সের নির্যাসে সিক্ত হয়ে। তাই, ২০১০: ওডিসি টু এল, সত্যিকার বৃহস্পতির প্রকৃতিকে তুলে ধরে।
এই দু উপন্যাসে আরো একটা বড় পার্থক্য আছে।
প্রথম উপন্যাস এবং চলচ্চিত্র প্রকাশিত হয় মানুষের ইতিহাস দ্বিখণ্ডিত হবার আগের ভাগে, চাঁদে পা রাখার আগেই। নীল আর্মস্ট্রং আর বাজ অলড্রিন নিরব সাগরে পা রাখলেন, ফিকশনের নতুন ধারার আবশ্যকতা বেরিয়ে এল। অ্যাপোলো এইটের চন্দ্রজয়ীরা আগেই চলচ্চিত্রটা দেখেছিলেন। চন্দ্রদেবের দূরপ্রান্তে মুগ্ধতার দৃষ্টি দেয়া প্রথম মানব চোখগুলো নাকি কী একটা খুঁজে বেড়িয়েছিল। তারা পরে আমাকে বলেছিলেন, তাদের চোখ চাঁদের বুকে কালো একটা প্রস্তর খুঁজেছিল এবং তারা সেটা আবিষ্কারের কথা প্রচারের জন্য মুখিয়ে ছিলেন।
হায়, এমন কোনোকিছুতো ছিল না সেখানে!
অ্যাপোলো তের মিশন আসলে ২০০১ এর সাথে কিছুটা যুক্ত ছিল বলা চলে। হাল কম্পিউটার যখন এই থার্টি ফাইভের ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করে তখন সে যে কথাটা ব্যবহার করেছিল তা হল, ‘আনন্দে বাধা দেয়ায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত; কিন্তু আমাদের একটা সমস্যায় পড়তে হল…’
যাক, অ্যাপোলো তেরোর কমান্ড মডিউলের নাম ছিল ওডিসি। মুভির বিখ্যাত জরথুস্ত্র থিমের মতো করে একটা টিভি সম্প্রচার এসেছিল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণের পর। তারা পৃথিবীতে যে কথাটা পাঠিয়েছিল, তা হল, ‘হিউস্টন, আমাদের একটা সমস্যায় পড়তে হল…’
লুনার মডিউলটাকে লাইফবোটে পরিণত করে মেধাবী পরিচালনার মাধ্যমে ওডিসিতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। নাসা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর টম পেইন আমার কাছে রিপোর্টটা পাঠানোর সময় কভারে লিখেছিলেন, ঠিক যেমনটা সব সময় আপনি বলে এসেছেন, আর্থার।
এমন আরো অনেক ঘটনা। মহাকাব্যিক যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ ওয়েস্টার-ছয় বা পালাপা বি-দুই এর ঘটনাও মিলে যায়। এগুলো মিসফায়ারিংয়ের কারণে ভুল কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছিল চুরাশি সালে।
কাহিনীর এক পর্যায়ে ডেভিড বোম্যানের ই ভি এ’র বাড়তি অংশ নিয়ে স্পেসশিপ ডিসকভারি থেকে বেরিয়ে গিয়ে হারানো পৃথিবীকে মূল ডিশ দিয়ে বিদ্ধ করতে হয়। (দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ডস অব ২০০১ এর ছাব্বিশতম অধ্যায়ে ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তর লেখাজোকা ছিল।) তারপর সে সেটা ধরতে পেরেও আসল কাজে ব্যর্থ হয়, এলোমেলো ঘোরা বন্ধ করতে পারে না।
চুরাশির নভেম্বরে নভশ্চর জো অ্যালেন স্পেস শাটল ডিসকভারি ছেড়ে বেরোন (না, কথাটা বানিয়ে বলছি না!) তারপর পালাপার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বোম্যানের সাথে তার একটাই পার্থক্য, ব্যাকপ্যাকের নাইট্রোজেন জেটের বা দিয়ে তিনি কাজটা করতে সফল হন।
ডিসকভারির কার্গো বে’ তে স্যাটেলাইটটা নিয়ে আসা সম্ভব হয়। তার দু’দিন পর ওয়েস্টারও উদ্ধার পায়। সে দুটিই ফিরে আসে পৃথিবীতে; আবার চেক করো, আবার ঠিক করো, আবার পাঠাও কালো আকাশে-এবার সফলতা; মানুষের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাস ছোট কিন্তু সাহসে ভরা দুর্দান্ত কাজ।
এখনো আমি ফুরিয়ে যাইনি। জো’র এই ঘটনার পর আমি একটা বই পাই হাতে, বইটার নাম, ‘অ্যান্টারিং স্পেস: অ্যান অ্যাস্ট্রোনট’স ওডিসি’, সেই সাথে মলাটে একটা লেখা ছিল:
প্রিয় আর্থার, আমি যখন ছোট্ট এক ছেলে, আপনি আমাকে লেখার পোকা আর স্পেসের পোকা-দুয়েই আক্রান্ত করেন। কিন্তু কেন বলেননি কাজ দুটো বাস্তবে করা কত্তো কঠিন!’
আমি আবেগে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ ধারার সংবর্ধনা আনন্দ দেয় অসীম, সেই সাথে রাইট ব্রাদার্সের মতো অনুভূতি এনে দেয়।
যে উপন্যাস আপনারা পড়তে যাচ্ছেন সেটা মাঝেমধ্যে ভালোভাবেই সমালোচিত হয়েছে। বিশেষত বিস্তর ব্যাখ্যা দেয়াটা একটু দৃষ্টিকটু ঠেকেছে সমালোচকের চোখে। সেই সাথে আরো একটা অভিযোগ, মুভির কয়েকটা রহস্যকে খোলাসা করে ফেলা হয়েছে। এমনকি রক হাডসন প্রিমিয়ারে বলেছিলেন, ‘ক্যান সামওয়ান টেল মি, হোয়াট দ্য হেল দিস ইজ অল অ্যাবাউট?
কিন্তু আমি মোটামুটি স্থির, বইতে সব সময়ই চলচ্চিত্রের চেয়ে একটু বেশি খোলাসা থাকা দরকার, এখানে শব্দ নেই, দৃশ্য নেই, তারপরও বেশি একাগ্রতা আছে। তারপরও আমি ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুললাম ২০১০ লিখে। (পরে পিটার হেইমস্ এটাকেও একটা দারুণ চলচ্চিত্রের রূপ দেন।) জটিলতা বাড়ালাম ২০৬১ লিখে, জটিলতা বাড়ালাম ৩০০১ লিখে।
কোনো ট্রিলজি’রই আসলে চারটার বেশি খণ্ড থাকা মানায় না। তাই প্রমিজ করতে পারি, ৩০০১ ই ফাইনাল ওডিসি।*
[* লেখক বেশিদিন প্রমিজ ধরে রাখতে পারেননি, সর্বজয়া মহাকাব্য এগিয়ে গেছে, অশীতিপর সর্বশ্রদ্ধেয় লেখক, স্পেস সায়েন্স ফিকশনের জনক আর্থার সি ক্লার্ক এই এখনো লিখছেন ওডিসি’র পঞ্চম পর্ব।]
প্রারম্ভ কথন
প্রতিটি জীবিত মানুষের সামনে এখন ত্রিশটা ভূত নেচে বেড়ায়। কারণ এখন জীবিত মানুষের সাথে মৃতদের অনুপাতটা এমনি। সময়ের জন্মের পর মোটা দাগে দশ হাজার কোটি মানুষ হেঁটে গেছে ধরিত্রীর এই পথ ধরে।
এখন, সংখ্যাটা আগ্রহ জাগায়। কারণ, আমাদের স্থানীয় সৃষ্টি জগৎ, স্থানীয় গ্যালাক্সি দুধসায়রে বা মিল্কি ওয়েতে কমবেশি এই সংখ্যক তারকাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো, এই পথে চলে যাওয়া প্রতি মানবের জন্য একটা করে নক্ষত্র আলোকদায়িনীর রূপ নিল।
কিন্তু তাদের প্রত্যেকেইতো আরাধ্য সূর্যদেব। বেশিরভাগই আমাদের কাছের নক্ষত্র, যাকে আমরা সূর্য বলে জানি তারচে অনেক অনেক বড়। এবং তাদের অনেকেরই, সম্ভবত বেশিরভাগেরই নিজস্ব আরাধনারত গ্ৰহজগৎ থাকার কথা। তাই, মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যকে অসীম জায়গা দেয়ার মতো যথেষ্ট স্থান এই এক জগতে আছে। সেই প্রথম বন-মানবের মতো একটা করে নিজস্ব, একেবারে একার ভূমি দিয়ে নিজের মতো বেহেস্ত বা দোজখ সাজিয়ে দেয়া কোনো কঠিন কাজ নয়।
সেই দূর, তারার দেশের সম্ভাব্য স্বর্গ বা নরকের মধ্যে ক’টায় এখন বসতি আছে? সৃষ্টির কোন্ কোন্ সিঁড়ি বেয়ে?
অনুমানের কোনো উপায় নেই। আমাদের পরের প্রজন্মের কাছে স্বপ্ন হয়ে থাকবে যে মঙ্গল বা শুক্র তাদের চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত সবচে কাছের তারকা-ভুবনটা।
কিন্তু দূরত্ব বিনাশী নয়, দূরত্ব নশ্বর। আমরা, মানবজাতি, একদিন মিলিত হব আমাদের সমকক্ষদের সাথে কিম্বা আমাদের স্বত্বাধিকারীর সাথে; তারার দেশ পেরিয়ে গিয়ে।
মানুষ নিজের অগ্রগতিকে মেনে নিতে বেশ অস্বস্তিতে ভোগে। কেউ এখনো আশা করে যে তারার দেশ ডিঙানো যাবে না। এমন ডিঙি আসবে না কখনো। কিন্তু দলে ভারি হতে থাকারা আজ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, এমন মিলন কেন হল না আজো, এখনো, যেখানে আমরা বেরিয়ে পড়তে শিখেছি স্পেসে?’
কেন নয়, অবশ্যই। সেই অতি বাস্তব প্রশ্নের একটা মোটামুটি সন্তোষজনক জবাব দেয়া যায়। কিন্তু মনে রাখবেন, এটা শুধুই এক কল্পনার জাতক।
বাস্তব, আর সব সময়ের মতোই, হবে আরো আরো অনেক অনেক অবিশ্বাস্য।
১. প্রচীন রাত্রি
প্রথম পর্ব – প্রচীন রাত্রি
অধ্যায় ১. ধ্বংসের পথ
এবারের অনাবৃষ্টি চলল কোটি বছর ধরে; এরও অনেক আগেই চারপেয়ে সরীসৃপ[১] সাম্রাজ্যের হয়েছে পতন। এই নিরক্ষীয় অঞ্চলটা অনেক অনেক পরে নাম পাবে আফ্রিকা। এই এখানে, অস্তিত্বের লড়াই পেয়েছে নিষ্ঠুরতার এক নতুন মাত্রা; কিন্তু আজো অস্তিত্ব-বিজয়ীর দেখা নেই। শূন্য, খটখটে মাটিতে একদম ছোট নয়তো একেবারে গতিময় নাহয় পুরোপুরি নির্দয়েরাই পারত বিবর্তনের ফুল ফোঁটাতে। বড়জোর দেখতে পেত বাঁচার ক্ষীণ আশা।
দিগন্তজোড়া তৃণভূমির বনমানুষেরা এসব বৈশিষ্ট্যের কোনোটা নিয়েই জন্মায়নি। তাই পারেনি বসুধাকে পুস্পিত করে তুলতে। এরই মধ্যে প্রজাতিগত অস্তিত্বের দৌড়ে পড়ে গেছে অনেক অনেক পেছনে। তাদের জনাপঞ্চাশেকের একটা দল একসারি গুহা দখল করে বসেছিল। গুহাটার পাশে জ্বলে পুড়ে খাক হওয়া এক উপত্যকা। ভ্যালিটাকে দুভাগ করেছে শামুক-গতির এক ছোট্ট উষ্ণ প্রসবণ। উত্তরে পাহাড়ের তুষার গলে যায়; দু’শ কিলোমিটার সর্পিল পথ পাড়ি দিয়ে নালাটা আসে এখানে। দুঃসময়ে প্রসবণটা উবে যেত একদম, গোটা জীবন টেনে চলত তৃষ্ণার ছায়ায় পিছলে গিয়ে।
এ উপজাতি চিরদিনই ক্ষুধার্ত ছিল, আজ তারা না খেয়ে মরতে বসেছে। সূর্যোদয়ের প্রথম ক্ষীণ আলোকমালা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে চাচ্ছে গুহার বুকে-এমন সময় চন্দ্র-দর্শী দেখে তার বাবা মরে পড়ে আছে রাতের আঁধারে। সে জানত না যে চির-বুড়োই তার বাবা। এসব সম্পর্ক তার উপলব্ধির অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। তবু সেই শুকনো শরীরটা দেখে একটু স্তব্ধ হয়ে যায়; এ অনুভূতিটা পরে নাম পাবে, কষ্ট।
দু’বাচ্চা এর মধ্যেই চেঁচাতে শুরু করেছে অন্নাভাবে। কিন্তু চন্দ্র-দর্শী মুখ ব্যাদান করে তাকাতেই তারা থেমে যায়। মায়েদের একজন দুধের বাচ্চাগুলোর পক্ষ নিল। মা বনমানুষীটা তাদের খাওয়াতেও পারেনি। কিন্তু মা-তো, তাই চন্দ্র-দর্শীর ধমকের জবাবে এক রাগ-ধরানো ভেঙচি কেটে দেয়। এই দু:সাহসের জবাব দেয়ার শক্তিও নেই পুরুষ বনমানুষ চন্দ্র-দর্শীর।
এবার যাবার মতো আলো এসেছে। গুহার ছাদ নিচু, তাই মাথা হেঁট করে চন্দ্র-দর্শী কুঁকড়ে যাওয়া লাশটা তুলে নিল। টেনে চলল নিজের পেছনে পেছনে। বাইরে বেরুতে পেরেই সে কাঁধের উপর শরীরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দু-পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়-এ ভুবনে একমাত্র প্রাণী, যে একাজটা করতে পারে।
নিজেদের মধ্যে চন্দ্র-দর্শী ছিল এক দৈত্য। লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট, অপুষ্টিতে জীর্ণ হলেও শত পাউন্ডের বেশি তার ওজন। ওর রোমশ পেশীবহুল শরীরটা মানুষ আর বানরের মাঝামাঝি। কিন্তু মাথাটা বনমানুষের চেয়ে মানবের দিকেই বেশি ঝুঁকে যায়। কপাল ততটা উঁচু নয়, অক্ষিকোটরের মধ্যে উঁচু ভাঁজ দেখা দিয়েছে; মানবতার বার্তা সে নির্ভুলভাবে বয়ে চলেছে নিজের জিনে। প্লেইস্টোসিন যুগের নির্দয় দুনিয়ার দিকে তাকাচ্ছে সে। তার অপলক দৃষ্টিতে এমন কিছু ধরা পড়ে যা আর কোনোদিন কোনো বনমানবের দৃকপাতে উঠে আসেনি। সেই কালো, গহীনে তলিয়ে যাওয়া চোখগুলোতে ভাসা-ভাসা একটু সচেতনতা খেলে যাচ্ছে-এটাই বুদ্ধিমত্তার প্রথম ঝলক যা হয়তো জন্ম-জন্মান্তরেও শিখার মতো জ্বলে উঠবে না; হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই তলিয়ে যাবে বিলুপ্তির অতলে।
বিপদের কোনো চিহ্ন নেই, তাই চন্দ্র-দর্শী গুহামুখের প্রায় খাড়া ঢালটা বেয়ে হাচড়েপাঁচড়ে যেতে থাকে; বোঝাটা তেমন কোনো সমস্যা নয়। বাকীরা যেন এই সংকেতের আশায়ই বসে ছিল। সকালের জলপানের জন্য সাথে সাথে বেরিয়ে গিয়ে এগুতে থাকে সেই কাদাপানির নালাটার দিকে।
চন্দ্র-দর্শী উপত্যকার অন্যপ্রান্তে দৃষ্টি ফেলে-যদি অন্যদের দেখা যায়; কিন্তু ওদের মাথার টিকিটারও দেখা নেই। হয় এখনো নিজেদের গুহা ছাড়েনি নয়তো ছুঁড়ে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের দূরপ্রান্তগুলো। কোথাও দেখা না যাওয়ায় চন্দ্র-দর্শী ভুলে যায় তাদের কথা; একসাথে একাধিক ব্যাপারে চিন্তা করতে সে আজো শেখেনি। তার মস্তিষ্কই অন্যরকম।
প্রথমেই তাকে চির-বুড়োর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে হবে। কিন্তু এ সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয় এক-আধটু। এ মরসুমে অনেক মৃত্যু এসেছে, একটা তার নিজের গুহাতেই; তার মানে তাকে লাশটা সেখানেই ফেলে আসতে হবে যেখানে ফেলে এসেছে নতুন-শিশু কে আকাশের চাঁদটার শেষভাগ বাকী থাকতে। বাকী কাজ সারবে হায়েনার দল।
এক জায়গায় এসে ছোট্ট উপত্যকাটা মিশে গেছে দিগন্তবিস্তৃত চারণক্ষেত্রের সাথে। হায়েনারা এর মধ্যেই প্রতীক্ষা শুরু করে দিয়েছে সেখানে। তার আসার কথা জানতে পেরেই ওরা অপেক্ষা করছে। চন্দ্র-দর্শী একটা ছোট্ট দেখে ঝোঁপের কাছে লাশটা ফেলে রেখে তড়িঘড়ি করে ফিরে যায় গোত্রের বাকীদের সাথে যোগ দিতে। আগের সব হাড়গোড় এর মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেছে। আর কোনোদিন নিজের বাবার কথা চন্দ্র-দর্শীর মনে পড়বে না।
সে, তার দু সাথী, অন্য গুহাগুলোর বয়েসীরা আর সব নবীন মিলে খাবার খুঁজে ফিরছিল খরায় শুকিয়ে যাওয়া গাছগুলোর আশপাশে। জায়গাটা উপত্যকার উপরদিকে। গুটি-গুটি ফল আর টসটসে লতাপাতা তাদের আরাধ্য। শিকড়বাকড় নাহয় হঠাৎ ভাগ্যে ঘটে যাওয়া গিরগিটি-ইঁদুর জাতীয় প্রাণীও তারা খোঁজে। একদম বাচ্চা আর অচল বুড়োদেরই শুধু গুহায় রেখে আসা হয়। যদি সারাদিনের চষে বেড়ানোর পর এক-আধটু খাবার বেঁচে যায় তো গুহায় ফেলে আসা বাকীদের খাদ্য পাবার সম্ভাবনা আছে। তা নাহলে হায়েনাদের কপালে শীঘ্রই আবারো ভালো কিছু জুটবে।
আজকের দিনটা ভালই-কিন্তু চন্দ্র-দর্শীর কোনো অতীত স্মৃতি নেই; এক সময়ের সাথে অন্যটার তুলনা সে করতে জানে না। এক মরা গাছের গোড়ায় মৌচাক পেয়ে গেল। সবচে মজার স্বাদটা নিতে পারবে ওরা এবার। ওর গোত্র এরচে সুস্বাদু কিছু চেনে না। শেষ বিকেলে দলটাকে ঘরে তাড়িয়ে নিতে নিতেও নিজের আঙ্গুলগুলো সে চেটে চলে বেখেয়ালে। অবশ্যই, বেশ ভালো পরিমাণে হুলের গুতো জুটেছে ওর কপালে; কিন্তু সেসময়ে ও এগুলোকে থোড়াই পরোয়া করত। এখন তার খিদে মোটামুটি তৃপ্তির দিকে হেলে পড়েছে, এরচে বেশি ক্ষুন্নিবৃত্তি কোনোকালে হয়নি-এখনো সে ক্ষুধার্ত হলেও আর খিদেয় কাহিল হওয়ার জো নেই। এই আধপেটা খাওয়াটাই কোনো বনমানুষের সারা জীবনে হাসিল করার মতো একমাত্র উদ্দেশ্য।
নালার কাছে যাবার সাথে সাথে তৃপ্তি উধাও হয়ে যায়। ওপাশে অন্যেরা। ওরা প্রতিদিনই সেখানে থাকে, কিন্তু বিরক্তির কিছুমাত্র কমে না কোনোদিন।
দলটায় ত্রিশজন। কিন্তু চন্দ্র-দর্শীর দল থেকে খুব একটা আলাদা বলে মনে হয় না। এ গোত্রটাকে আসতে দেখেই ওপাশের ওরা উদ্বাহু নৃত্য শুরু করে। হাত ঝকায়, নিজেদের পাশের নালার মাটিতে আঘাত করে চলে। এপাশের ওরাও একই কায়দায় জবাব দেয়।
শুধু একুটুই হয়। কালেভদ্রে বনমানুষেরা একে অন্যের সাথে লড়ে, কুস্তি করে। তাদের খুনসুটিতে দুর্ঘটনা ঘটে খুব কমই। কোনো নখর নেই, নেই তীক্ষ্ণ দাঁত। তার উপর শরীর জুড়ে আছে প্রতিরক্ষার ভারি লোম। একে অন্যের তেমন কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। যেভাবেই বলা হোক না কেন, এ ধরনের অনুৎপাদনশীল কাজে খরচ করার মতো বাড়তি শক্তি তাদের থাকে খুবই কম। তর্জনগর্জনই তাদের সার। শুধু নিষ্ফল আক্রোশ দেখানোর কাজটা নিরাপদ আর সুন্দর।
যুদ্ধংদেহী ভাব চলল পাঁচ মিনিটের মতো, তারপরই যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছে তেমন করে শেষ হয়ে যায় প্রদর্শনী। শেষে প্রত্যেকে পেটপুরে শুষে নেয় কাদাজল। জরুরী কাজ শেষ। আত্মা শান্তি পেয়েছে, এবার যার যার পথ ধরে তারা। গুহা থেকে মাইলখানেক দূরে সবচে কাছের চারণভূমি, সেটাকে ভাগাভাগি করে নিতে হবে বিশালদেহী অ্যান্টিলোপের মতো জানোয়ারের সাথে। সেসব জন্তু পরোয়া করে ওদের থাকা-না থাকাকে। প্রাণীগুলোকে সরিয়ে দেয়া যায় না, কারণ ওরা মাথায় ভয়াবহ ভোজালী-তলোয়ার নিয়ে রণসজ্জায় সজ্জিত। এই শিংয়ের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ বনমানুষদের নেই।
তাই চন্দ্র-দর্শী আর ওর সব সাথী মিলে চিবিয়ে বেড়ায় বেরী, শুকনো ফল আর লতাপাতা; তীব্র জ্বালার সাথে যুদ্ধ করে চলে। অথচ তাদের চারপাশের এসব প্রতিযোগীর সাথে ভাগজোখ করে তৃণ খেয়ে বেড়ানোর কথা না। সেসব প্রাণীই হতে পারত অফুরান, অকল্পনীয় খাদ্যের নিশ্চিত ভাণ্ডার। এই এখনো চারণভূমিতে চড়ে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার টন সুস্বাদু মাংসের উৎস কিন্তু এ গোস্তের তালকে নিজের মনে করার কাজ শুধু তাদের জন্য অসম্ভবই নয়, অকল্পনীয়। প্রাচুর্যের ভেতর ডুবে থেকেও ওরা তলিয়ে যাচ্ছে মৃত্যু আর অবলুপ্তির অতল গহ্বরে।
গোধূলীর আলোয় তেমন কোনো ঘটনা ছাড়াই গোত্রটা ফিরে এল গুহার দিকে। আহত যে বুড়ো বনমানুষীটাকে ওরা ছেড়ে গিয়েছিল সেটা তৃপ্তির মৃদু শব্দ তলে। কারণ চন্দ্র-দর্শী একটা বেরীভর্তি ডাল এগিয়ে দিয়েছে। বনমানুষীটা সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটার উপর। এখান থেকে খুব কম পুষ্টিই জুটবে কিন্তু এটুকুই ওকে বেচে থাকতে সাহায্য করবে। সহায়তা করবে চিতার আঘাত থেকে সেরে উঠতে, আবার খাদ্যের খোঁজে যেতে।
উপত্যকার ওপাশ থেকে উঠে আসে পূর্ণিমার চাঁদ, কোন্ দূরের পাহাড় থেকে নেমে এসে হিম-হিম বাতাস বয়ে যায়। আজ রাতে দারুণ ঠাণ্ডা পড়তে পারে, কিন্তু খিদের মতো শীতও তেমন কোনো বাস্তব উদ্বেগের কারণ নয়; এ হল জীবনের পেছনে চিরায়ত চিত্রপট।
নিচের দিকের কোনো গুহা থেকে হুংকার আর আর্তনাদ ভেসে আসছে দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে। চন্দ্র-দর্শী স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। এখন আর চিতার সেই মাঝেমধ্যে শোনা গর্জনের জন্য ওর অপেক্ষা করার দরকার নেই। ও ঠিক ঠিক জানে কী হচ্ছে সেখানে। সাদা চুলের বুড়ো আর ওর পরিবার লড়তে লড়তে মারা পড়ছে। সাহায্যের চিন্তাটা কখনোই চন্দ্র-দর্শীর মাথায় আসে না; বেঁচে থাকার নগ্ন নিয়মগুলো এতই কঠিন। পুরো পাহাড়ের কোথাও প্রতিবাদের একটা চিৎকার প্রতিধ্বনি ওঠে না। প্রত্যেক গুহাতেই মরণ-নিস্তব্ধতা, নয়তো চেঁচামেচি করলে নিজের গিরিগর্তটাও আক্রান্ত হতে পারে।
অনিশ্চয়তা কেটে গেছে। পাথরের উপর দিয়ে শরীর টেনে নেয়ার শব্দ শুনতে পায় চন্দ্র-দর্শী। মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই চিতাটি নিজের শিকার উপভোগের মতো উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেল। এ কাজে তেমন শক্তি ব্যয় হয় না। নিরবতায় চিড় ধরে না। সহজেই বাঘটা নিজের চোয়ালে ঢুকিয়ে দিতে পারে শিকারকে।
আরো দু-চারদিন এখানে ঝুঁকি থাকবে; কিন্তু আরো শত্রু থাকতে পারে আশপাশে যারা এই শীতল, ফ্যাকাশে, নিশি-সূর্যের সুযোগ নিতে চায়। ঠিকমতো সবাই জানতে পারলে চেঁচামেচি করে ছোট শিকারীগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে চন্দ্র-দর্শী বেরিয়ে আসে, উঠে যায় প্রবেশ পথের একটা পাথরের উপর। সেখান থেকেই নজর রাখে উপত্যকায়।
সব যুগে, সব কালে পৃথিবীর বুকে এগিয়ে চলা সব প্রাণীর মধ্যে বনমানুষেরাই প্রথম চাঁদের দিকে আগ্রহ নিয়ে মূর্তির মতো চেয়ে থাকতে শিখেছে। তার মনে নেই, যখন ছোট ছিল তখন প্রায়ই পাহাড়ের পেছন থেকে ওঠা এই ভৌতিক অবয়বটাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতো।
ও কখনোই সফল হয়নি। আর আজতো ব্যাপারটা বোঝার মতো যথেষ্ট বড়। রাতের সূর্যকে ধরতে হলে প্রথমে অবশ্যই ওকে বিরাট কোনো গাছ বেয়ে উঠে যেতে হবে।
সময় সময়ে সে খুঁটিয়ে দেখত ভ্যালিটাকে। দেখত আকাশের চাঁদ। কিন্তু সব সময় আর একটা কাজ করত-তা হল খেয়াল দিয়ে শোনা। দু-চারবার ছাড়া সর্বদা সে ঘুমায় টান-টান স্নায়ুকে জাগিয়ে রেখে। খরকুটো পতনের শব্দও তাকে বিরক্ত করার জন্য যথেষ্ট। পঁচিশ বছরের মতো বয়সেও সবটুকু ক্ষমতার উপর দখল ধরে রেখেছে নিজে। ওর ভাগ্য সহায় হলে, দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে পারলে, রোগ-ব্যাধি শিকারী-ক্ষুধাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে আরো বছরদশেক বেঁচে থাকবে।
রাত নেমেছে। শীতল, স্বচ্ছ, বেপরোয়া। আর কোনো বিপদসংকেত নেই। চাঁদ উঠে এসেছে ধীরে ধীরে নিরক্ষীয় এলাকার পেছন থেকে। অপরূপ এ দৃশ্য কোনো মানুষের চোখ কোনোদিন দেখতে পায়নি। আর পর্বতের গর্তগুলোয় বাধা পাওয়া ঘুম এবং ভয় ধরানো প্রতীক্ষার মাঝেও জন্ম না নেয়া প্রজন্মের দু:স্বপ্নেরা জন্ম নেয়।
এদিকে দ্বিতীয়বারের মতো আকাশের একপাশ থেকে আরেক পাশে যাবার সময় ঠিক মাথার উপর দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলে একটা কিছু। জ্বলজ্বলে এক আলোর বিন্দু। যে কোনো তারার চেয়ে অনেক বেশি আলোময়।
অধ্যায় ২. নব্য প্রস্তর
রাত, ফুরনোর আগেই অকস্মাৎ সচকিত হয়ে জেগে ওঠে চন্দ্র-দর্শী। সারাদিনের ধকলের পর আজ একটু বেশিই পড়ে-পড়ে ঘুমাচ্ছিল সে। উপত্যকার পথ ধরে প্রথম মৃদু ধ্বনি ওর কানে পৌঁছে যায়।
গুহার পুতিগন্ধময় আঁধার পরিবেশে উঠে বসে সে। নিজের সবটুকু অনুভূতিকে ফিরে পেতে কসরৎ করে, তারপর আচমকা ওর মনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে আতঙ্ক। ওর বয়স এর মধ্যেই গোত্রের বাকীদের আকাঙ্ক্ষার জীবদ্দশা থেকে দ্বিগুণ। এত দীর্ঘ জীবনেও সে কক্ষনো এমন অলুক্ষনে শব্দ শোনেনি। বিড়াল গোষ্ঠীর বড় প্রাণীগুলো নিরবে উঠে আসে। ওদের ধোকা দেয়ার সাধ্য শুধু ভূমিকম্পেরই আছে। মাঝেমধ্যে ডালপালার ভেঙে পড়ার শব্দও শোনা যায়। অথচ এ আওয়াজ ক্রমাগত ভাঙনের মতো। ধীরেসুস্থে আরো প্রবল হচ্ছে। গায়-গতরে বিশাল কোনো প্রাণী যেন রাতের বেলা ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজেকে গোপন করার কোনো চেষ্টা না করেই। বেপরোয়া। একবার চন্দ্র-দর্শী ঝোঁপঝাড় উপড়ে ফেলার শব্দ পেয়েছিল ঠিক ঠিক। এসব অকাজ হাতি আর ডায়নোথেরিয়ারা[৪] মাঝেমধ্যেই করে বসে। কিন্তু অন্য সময় তারাতো একদম বেড়ালের মতো নিঃশব্দ।
এবার এমন এক শব্দ আসে যেটা চন্দ্র-দর্শী চিনতে পারেনি। কারণ এর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো ওঠেনি এমন আওয়াজ। পাথুরে জমির বুকে ধাতব জিনিসের আছড়ে পড়ার শব্দ এটা।
ভোরের প্রথম আলোয় নিজের উপজাতি নিয়ে নিচের তটিনীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় প্রথমবারের মতো চন্দ্র-দর্শী নতুন পাথর এর মুখোমুখি হয়। রাতের বীভৎস ভয়ের কথা এর মধ্যেই বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে মন থেকে, কারণ সেই শব্দের পরপর কোনো কিছু হয়নি। তাই সে এই অদ্ভুতুড়ে জিনিসের সাথে বিপদ বা ভয়ের কোনো সম্বন্ধ পাতানোর চেষ্টাই করে না। হাজার হলেও, এ নিয়ে সতর্ক হবার মতো কিছু পাওয়া যায়নি।
জিনিসটি চৌকো আর নিরেট। লম্বায় চন্দ্র-দর্শীর চেয়ে কম করে হলেও তিনগুণ, তবে প্রস্থের হিসাবে দু-হাতে আটকে দেয়া যাবে। জিনিসটা একেবারেই স্বচ্ছ কোনোকিছুতে তৈরি। এর প্রান্তগুলোয় সূর্যালোক পড়ে ঠিকরে না বেরুলে অস্তিত্ব বোঝা যেত না। চন্দ্র-দর্শী জীবনেও বরফের মুখোমুখি হয়নি। দেখেনি স্ফটিক স্বচ্ছ জল। কোনো প্রাকৃতিক জিনিসের সাথেই এই ভুতুড়ে গড়নের তুলনা চলে না। হঠাৎই যেন খুব আকর্ষণীয় মনে হয় তার কাছে। ও যথেষ্ট সতর্ক। তবু এর চারপাশে ঘুরে বেড়াতে তেমন সময় নেয় না। যেন কিছুই হয়নি। হাত রাখে এর গায়। ঠাণ্ডা আর শক্ত একটা উপরিতল অনুভব করে সে।
কয়েক মিনিটের ইতস্তত ভাবনার পর এক দারুণ সমাধান মাথায় চলে এল। এটা এক পাথর, অবশ্যই পাথর। জন্মেছে রাতের মধ্যেই। অনেক গাছই এমন সব কাণ্ড করে বসে। সাদা, ফলের কাছাকাছি আকৃতির জিনিসগুলো রাতের প্রহরে প্রহরেই গজিয়ে ওঠে। কথা সত্যি, ওগুলো অনেকটাই ছোট, দেখতে গোলপানা। এদিকে এটা বিরাট আর প্রান্তগুলো ধারালো। হায়, চন্দ্র-দর্শীর অনেক পরের আরো বড় বড় দার্শনিক বিশাল বিশাল সব তত্ত্ব নিয়ে এর সামনে হাজির হলেও বোধ হয় একইভাবে বিনা সমাধানে আহত হয়ে ফিরে যাবে।
এই অসাধারণ চিন্তাই চন্দ্র-দর্শীকে পরের তিন-চার মিনিটের মধ্যে এক যুগান্তকারী কাজে প্রবৃত্ত করল। শিঘি এর স্বাদ নিয়ে নেয়া ভালো। পাথরের মতো দেখতে সেসব সাদা গোলগাল গাছ খেতে ভারি মজা (অবশ্য দু-চারটে এমনও মিলে যায় যা অসুখ দিয়ে কাবু করে তোলে); যতটুকু বোঝা যায়, এই লম্বাটাও…?
দু-চারবার চেটে নিয়ে কামড়াতে গিয়েই ও মিথ্যা আশার প্রহেলিকা থেকে মুক্তি পেল। এখানে কোনো পুষ্টির চিহ্নও নেই। সুতরাং একজন সজ্ঞান বন মানবের মতো সে নিজের দল নিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে যায়। অন্যদের দিকে চেয়ে নর্তনকুর্দনের পবিত্র দায়িত্বটা পালনের সময় ভুলে যায় স্ফটিক স্বচ্ছ একশিলার সবটুকু কথা।
আজকের খোঁজাখুজি একদম বৃথা। কোনোমতে এক-আধটু খাবার যোগাড় করতে তাদের চষে বেড়াতে হয় গুহা থেকে দূরের বেশ কয়েক মাইল এলাকা। দুপুরের নির্দয় রোদে এক হাড্ডিসার বনমানবী ভেঙে পড়ে। যে কোনো সম্ভাব্য আশ্রয় থেকে অনেক দূরে তারা। চারদিকে জড়ো হল সাথীরা। অবোধ শোকের শব্দ করল। এটুকুই, এরচে বেশি কিছু করার নেই কারো। আর একটু কম পথশ্রান্ত হলেই নিজেদের সাথে বয়ে বেড়াতে পারত। কিন্তু এত বড় দয়া দেখাবার মতো শক্তির যোগান নেই ওদের। তাকে ফেলেই এগুতে হবে। খাদ্য পেয়ে উঠে না এলে নিজের বাকী সম্বলটুকুও খাবারে পরিণত হবে।
বাড়ি ফেরার পথে সে জায়গাটা ওরা পেরিয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা একটা হাড়ও খুঁজে পাওয়া যায় না।
দিবসের শেষ আলোয় দলটা আগের পানি-শিকারীদের খোঁজে ইতিউতি তাকাতে তাকাতে তড়িঘড়ি করে পানিতে গলা ভিজিয়ে নিয়ে নিজেদের গুহাপথে ফিরে যেতে শুরু করে। কিম্ভুত শব্দটা শুরুর সময় ওরা নতুন পাথর থেকে শত কদম দূরেই ছিল।
স্পষ্ট শোনা যায়। বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে যায় ওরা। যেন অসাড়ত্ব সারা শরীরকে দখল করে নিয়েছে। যার যার পথেই চোয়াল ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা সাধারণ, উন্মাদনাময় তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে ক্রিস্টাল থেকে। এর জাদুর আওতায় পড়া সবাইকে করে তুলছে সম্মোহিত। প্রথমবারের মতো, এবং শেষবারের মতো, তিন মিলিয়ন বছরের জন্য-আফ্রিকার কালো বুকে ঢাকের মৃদুমন্দ বজ্রনিনাদ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে।
কাঁপন আস্তে ধীরে বাড়তেই থাকে, আরো তালে তালে, আরো তালে তালে। এবার অরণ্য মানবেরা সামনে চলতে শুরু করেছে। যেন নিশিতে পাওয়া মানুষ। সামনে•সেই তরঙ্গায়িত শব্দের উৎস। মাঝেমধ্যে এক-আধটু নাচের মোহনীয় ধীরলয়ের ভঙ্গিমা নেয় পদক্ষেপগুলো। তাদের প্রতিটা রক্তকণা উল্লসিত হয়ে উঠেছে। সাড়া দিয়ে চলেছে বহু জনম পরের উত্তেজনার পথে। পুরোপুরি কাছে যাবার পরই সবাই ঘিরে ধরে মনোলিথটাকে। দিবসের সবটুকু ক্লান্তি ওরা ভুলে বসেছে; ভুলে বসেছে আসন্ন গোধূলীর ভয়াল চেহারা আর ক্ষুৎপিপাসার জান্তব জ্বালার কথা।
ঢাকের শব্দ আর রাতের অমানিশা আরো আরো বেড়ে যায়, হয় দ্রুততর। ছায়াগুলো দিগন্ত ছোঁয়া শুরু করলে, সবটুকু সূর্যালোক শোষিত হলে সেই স্ফটিক ছড়াতে শুরু করে আলোর ছটা।
প্রথমে স্বচ্ছতা হারায়। ধারণ করতে থাকে একটু রঙের আবেশ, দুধরঙা ঔজ্জ্বল্য উদ্ভাসিত করে চারদিক। অবোধ্য, অব্যাখ্যাত ভূতেরা দাবড়ে বেড়ায় এর উপরিতল থেকে গভীরে, গভীর থেকে উপরে। হঠাৎ করেই আলো-আঁধারীর রেখায় বিভক্ত হয়ে একদেহী হয়ে ওঠে ওগুলো। পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বৃত্তাকার ক্রমঘূর্ণায়মান আকার দেয়।
আলোক চক্র আরো আরো দ্রুত ঘুরে চলে। ঢাকের গুড়গুড় আওয়াজ এর সাথে সাথে বেড়ে চলেছে। এখন অকল্পনীয় সম্মোহিত বন মানুষেরা হাঁ করে চেয়ে থাকতে পারে শুধু এই আগুনে খেলার দিকে। নির্নিমেষ। এরমধ্যেই ভুলে বসেছে বংশগত সব অর্জনের কথা, সতর্কতার কথা। বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে জীবনব্যাপী পাওয়া সেসব আত্মরক্ষার শিক্ষা। শুধু তাদের কোনো একজন নয়, সবাই। যেন গুহাগুলো অনেক অনেক দূরে, যেন সেই কষ্টকর বিকাল থেকে তারা বহু যোজন সরে এসেছে। আশপাশের ঝোঁপঝাড় জ্বলজ্বলে চোখের শ্বাপদে গেছে ভরে। রাতের সৃষ্টিরা অনড় বসে আছে, এর পরের ঘটনার জন্য প্রতীক্ষারত।
এবার আলোকমালা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। চক্রের ভিতরের রেখাগুলো আলোয় ভাসা দাগে ভাগ হয়ে যায়। অরণ্য মানবের মতো সেগুলোও চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এবার দাগগুলো বিভক্ত হয়ে যায় জোড়ায় জোড়ায়। ফলে উজ্জ্বল জোড়গুলো একে অন্যকে অতিক্রম করে দোলায়িত হতে থাকে। পরস্পরকে ছেদ করার বিন্দু বদলাতে থাকে আস্তে আস্তে। যখন জ্বলজ্বলে খণ্ডগুলো একত্র হয়, আবার যখন হয় আলাদা তখন অসাধারণ ভাসন্ত জ্যামিতিক প্যাটার্নগুলো অস্তিত্বের ভিতর-বাহিরে আলোর ঝলক খেলিয়ে চলে। আর বনের মানুষেরা সেসব বন্দী আলোকোজ্জ্বল জিনিসের কান্ড কারখানা আটকে নেয় নিজের নিজের মনে।
কখনো হয়তো তারা বুঝবে না যে তাদের মনগুলোকে নিরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে, এঁকে নেয়া হয়েছে তাদের শরীর, প্রতিক্রিয়ার পল-অনুপল পাকাপাকিভাবে তুলে নেয়া হয়েছে, মাপজোক নেয়া হয়েছে তাদের সবটুকু শক্তি, ক্ষমতা আর সম্পদের। প্রথমেই পুরো উপজাতিকে আধা নত করা হয়। তারা জমাট পাথরের মতো নিথর। এবার স্বচ্ছ স্ফটিকের সবচে কাছের বনমানুষটা অতর্কিতে জীবন ফিরে পায়।
নিজের জায়গা থেকে একটুও নড়েনি। কিন্তু শরীরটা বিমোহিত অবস্থান থেকে সরে আসে। আড়ষ্টভাবে নড়েচড়ে ওঠে, যেন কোনো এক অদৃশ্য খেলুড়ের হাতের পুতুল। অদৃশ্য সুতো যেন চারধারে বিছানো। মাথা একবার এদিক তো আরেকবার ওদিকে নড়ে উঠছে। নিঃশব্দে মুখ খুলেই বন্ধ হয়ে যায়। হাত মুঠো পাকায়, আবার যায় খুলে। এবার শরীর ভাঁজ হয়ে গেল নিচের দিকে। একটা লকলকে ঘাসের ডগা আনল তুলে। অপ্রস্তুত আঙুলগুলো একটা গিট পাকানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
তাকে দেখে মনে হয় একটা ব্যাপারে সে লড়ে চলেছে নিরন্তর। কোনো এক অদেখা নিয়ন্তার হাত থেকে নিজের শরীরটাকে মুক্ত করার প্রাণান্ত প্রয়াস দেখা দেয় তার অভিব্যক্তিতে। বাতাসের জন্য আঁকুপাঁকু করে বেড়ায় ফুসফুস, অপার্থিব আতঙ্ক নগ্ন হয়ে ফুটে ওঠে সারা চোখমুখে। অবর্ণনীয় জান্তবতায় চেষ্টা চালিয়ে যায় আঙুলগুলোকে দিয়ে এমন জটিল কোনো কাজ করাতে যা ইহধামে আর কেউ কোনোকালে করেনি।
নিজের সর্বশক্তি দেবার পরেও পাতাটাকে শুধু দ্বিখণ্ডিত করে বসতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। টুকরোগুলো মাটি ছুঁয়ে দেয়ার সাথে সাথেই নিয়ন্তা শক্তি তাকে ছেড়ে যায়। সে ফিরে যায় অনড় অবস্থায়।
এবার জীবিত হয় আরেক বনমানুষ। সেও একই কাজ করার চেষ্টা করে। বয়সে নবীন হওয়ায় একে দিয়ে কাজ করানো সহজ হচ্ছে। সহজেই তার হাতের ঘাসের ডগাটা বাঁক খায়, একের ভিতর অন্য প্রান্ত প্রবেশ করে। অপেক্ষাকৃত বয়েসীটার ব্যর্থতার উপরেই সে সাফল্যের ঝাণ্ডা ওড়ায়। বসুধার বুকে প্রথমবারের মতো কোনো জটিল বন্ধন সৃষ্টি হল…।
অন্যেরা আরো সব অস্বাভাবিক, আপাতত অর্থহীন কাজ করে চলে। কেউ হাত দুটোকে ছড়িয়ে দেয় যথাসম্ভব। একবার দুচোখ খুলে, আরেকবার একটা বন্ধ করে; কেউবা আঙুলের ডগাগুলোকে পরস্পরের সাথে লাগিয়ে নিতে চায়। কাউকে আবার সেসব আলোক কাঠির দিকে চেয়ে থাকতে হয় পলকহীনভাবে। কাঠিগুলো আরো বিভক্ত হয়, আরো ভাগ হয়ে যায়। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর রেখায় বিলীন হয়ে যায়। আবার সবাই শুনতে পায় এক অখণ্ড শব্দের ঢেউ। সেটাও সূক্ষ্ম হয়ে হয়ে হারিয়ে যায় শব্দের[৫] তরঙ্গে।
চন্দ্র-দর্শীর পালা এলে ও ভয় পায় খুব কমই। তার সবচে বড় অনুভবটা সামান্য ব্যথার মতো। যেন আঘাত পেয়েছে কোথাও। পেশীগুলো হঠাৎ নড়েচড়ে ওঠে, হাত পা এমন কোনো আদেশে নড়ে যা ঠিক তার নয়।
কারণ না জেনেই সে উবু হয়ে তুলে নেয় একটা ছোট্ট পাথর। উপরে উঠেই দেখতে পায় স্বচ্ছ স্ফটিকের কোথাও একটা নতুন গড়ন ফুটে উঠেছে।
সেসব রেখা, নাচতে থাকা চক্র, সব উধাও। তার বদলে ছোট থেকে বড় বৃত্তের দলকে দেখা যায় একের উপর এক পড়ে থাকতে। পানিতে হাত ডোবালে যেমন ঢেউ ওঠে, তেমন। ঠিক মাঝে একটা কালো, ছোট্ট চাকতি।
মস্তিষ্কে আসতে থাকা নিরব আদেশ পালন করে চন্দ্রদর্শী পাথরটাকে মাথার উপরে তোলে, লক্ষ্য বরাবর দেয় ছুঁড়ে। পাথরটা লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করেনি।
আবার করো-সেই আদেশ এল। আরেক পাথর পাওয়ার আগ পর্যন্ত সে ছুঁড়ে বেড়ায় আশপাশটা। এবার সশব্দে সেটা আছড়ে পড়ে টার্গেটের উপর। রিনিঝিনি ঝংকার ওঠে সেদিক থেকে। এখনো অনেকদূরে সে, কিন্তু উন্নতি হচ্ছে কাজের ক্ষেত্রে।
চারবারের বেলায় সে কেন্দ্রের চোখটা থেকে কয়েক সেন্টিমিটার দূরে পাঠাতে পারে প্রস্তর খণ্ডকে। অপার্থিব বর্ণনাতীত কোনো আনন্দের ঢেউ খেলে গেল এবার তার মনে; প্রায় শারীরিক তৃপ্তির মতো একটা ব্যাপার। এবার একটু ঢিল পড়ে নিয়ন্ত্রণে। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুর তাগাদা অনুভব করছে না চন্দ্র-দর্শী।
একের পর এক গোত্রের সবাইকেই পরীক্ষা করে নেয়া হচ্ছে। কদাচিৎ কেউ সফল হয়, বেশিরভাগই নিজেকে দেয়া কাজটা করতে পারে না ঠিকমতো। আর সবাইকেই উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হচ্ছে, ব্যথা নয়তো আনন্দ।
এবার সেই নব্য প্রস্তরে দেখা দেয় একদেহী নিরাকার আলোর ছটা। যেন চারদিকের আঁধার রাজ্যে এ এক মহামহিম আলোকবর্তিকা। ঘুমের ঘোর কাটার মতো করে তাদের মোহভঙ্গ হল। এবার তারা নিরাপদ আশ্রয়ের পথে চলতে থাকে দুলকি চালে। পেছন ফিরে তাকায়নি। তাকালে অবাক চোখে দেখতে পেত, কোনো এক অদ্ভুত আলো তাদের বাড়ির পথ দেখিয়ে চলেছে- দেখিয়ে চলেছে অদেখা অচেনা ভবিষ্যতের রাজপথ।
অধ্যায় ৩. শিক্ষালয়
চন্দ্র-দর্শী আর ওর সাথীদের সেসব স্মৃতির কোনোটাই মনে পড়ে না; সেই ক্রিস্টাল, তারপরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কাজ করানো-কিছুই না। পরের দিন খাবারের খোঁজে বেরুনোর পরে তারা পাথরের সামনে সামান্য সময়ের জন্যও থমকে দাঁড়ালো না। এখন এটা তাদের স্মৃতির ধূসর, বিবর্ণ, মুছে যাওয়া অংশের অন্তর্গত। ওরা এটাকে খেতে পারবে না, এরও কোনো ক্ষমতা নেই ওদের গলাধঃকরণ করার। সুতরাং কোনো পক্ষ থেকে ক্ষুধা জনিত-সম্পর্ক না থাকায় এর কোনো গুরুত্বই নেই।
পাতলা নদীটার ওপারে সেই অন্যেরা নিজেদের নিষ্ফল আক্রোশ ঢেলে যাচ্ছে। তাদের নেতা এক কানওয়ালা। বয়েস আর আকার প্রকারে চন্দ্র-দর্শীর মতোই। শুধু বেচারার হাল-হকিকত আরো খারাপ। নিজের এলাকায় একটু নেচেকুদে বেড়ায়, রক্তহিমকরা চেঁচামেচির চেষ্টা চালায়। নিজের সাহসকে আরেকটু শক্তি আর অন্যদলকে ভড়কে দেবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত ঝাঁকিয়ে যায় দুই বাহু। আজ ঝরা পানির প্রবাহ কোথাও কোথাও ফুটখানেক গভীর। কিন্তু এক কানওয়ালা টা এর মাঝেই দাবড়ে বেড়াচ্ছে। আরো বেশি রেগে উঠছে, উঠছে আরো তেতে। ধীরেসুস্থে সে প্রায় নিথর হয়ে আসে। তারপর পিছিয়ে গিয়ে সাথীদের সাথে যোগ দেয় জলপানে।
এটুকু ছাড়া প্রাত্যহিক নিয়মের কোনো পরিবর্তন নেই। সেদিনের মতো খোঁজাখুঁজি শেষ। আরো একটা দিনের চলনসই পুষ্টি জুটে গেল। কেউ মারাও পড়েনি।
সে রাতেও স্ফটিক স্বচ্ছ গড়নটা অধীর অপেক্ষায় রত। চারপাশে সেই আলো আর শব্দের ইন্দ্রজাল। এবারের কাজটা আরো নিখুঁত। ভিন্নতর।
বেশ কয়েকটা বনমানুষকে সে পুরোপুরি অবজ্ঞা করে। যেন সবচে সম্ভাবনাময় পাণিগুলো নিয়েই এর যত উদ্বেগ। চন্দ্র-দর্শী তাদেরই একজন। আবারো সে মস্তিষ্কের অব্যবহৃত অংশগুলোয় অচিন প্রবাহ অনুভব করে। এবার সে দেখতে লাগল দারুণ সব দৃশ্য।
দৃশ্যেরা হয়তো ক্রিস্টাল মনোলিথটার ভিতরেই আছে, নয়তো তার নিজের মনের গহীনে। কে জানে? আসল কথা হল, চন্দ্র-দর্শীর চোখে সেগুলো একেবারে বাস্তব। আবারো তার সহজাত সব প্রবৃত্তি দৌড়ে পালায় নিজের কাছ থেকে।
ও একটা দারুণ শান্তিতে থাকা পারিবারিক দল দেখতে পাচ্ছে। ওর চেতনার সেই চিরচেনাদের থেকে আপাতত একটা মাত্র পার্থক্য ধরা পড়ে। ভোজবাজির মতো উদয় হওয়া সেই পরিবারের একজন পুরুষ, এক নারী ও দুই শিশু আছে। তারা শান্তভাবে আয়েশী ভঙ্গিতে খেয়ে চলেছে। মোটাসোটা, চর্বিজমা, চকচকে দেহ তাদের। এটা জীবনের সেই ধারা যা চন্দ্র-দর্শীর মনশ্চক্ষুতে কোনোকালে ধরা। দেয়নি। অচেতনভাবেই নিজের শিরদাঁড়ায় ও দৃষ্টি দেয়-এই প্রাণীগুলোর মেরুদন্ড আর বুকের পাঁজর চর্বিতে ঢাকা। সারাক্ষণ তারা অলসভাবে বসে থাকে। কত সহজেই নিজের গুহার চারপাশে রাজত্ব করে চলে! সারা দুনিয়ার সবটুকু শান্তি ভর করেছে তাদের উপর। এক আধবার পুরুষ প্রাণীটা কেমন অপার তৃপ্তিতে ঢেকুর তুলছে।
আর কোনো কাজকর্ম নেই। পাঁচ মিনিট পরে সেই সচেতনতা কেটে গেল। এবার আর ক্রিস্টালটাকে অন্ধকারের একটা আকৃতি ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না; আবারো চন্দ্র-দর্শী নিজেকে স্বপ্নভঙ্গের পর খুঁজে পায়। হঠাৎ করেই নিজের অবস্থান বুঝতে পারে, তাড়িয়ে চলে দলকে গুহার দিকে।
যা দেখেছে তার তেমন কোনো সচেতন স্মৃতি ওর মানসপটে নেই। কিন্তু সেই রাতে নিজের গুহার উষ্ণতায় বসে থাকার সময় চারপাশের দুনিয়ার সবটুকু শব্দের সাথে নিজেকে সচেতন করে নেয় সে। চন্দ্র-দর্শী এই প্রথম কোনো নতুন ধরনের অনুভূতির খোঁজ পেয়েছে। পায়ে পায়ে অনুভূতিটার এগিয়ে আসার আওয়াজ শুনতে পায় সে। কোন্ গহীন থেকে উথলে আসে ঈর্ষার অপূর্ণ আর প্রাচীনতম আবেগ। নিজের জীবনের অসফলতার জ্বালা আসে। এর কারণ সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাই নেই। এখনো এতে তেমন কিছু যায় আসে না। তার আত্মায় বাসা বেঁধেছে অতৃপ্তি। এভাবেই চন্দ্র-দর্শী প্রথমবারের মতো মানুষ’ এর পথে ছোট্ট কদম ফেলল।
রাতের পর রাত সেই চার তৃপ্ত অরণ্য মানবের দৃশ্য দেখানো হয় যে পর্যন্ত ভিতরে বসে না যায় দৃশ্যগুলো; যে পর্যন্ত ক্ষুধারই মতো রক্তে মিশে না যায়। শুধু নিজের চোখে দেখলে এমন প্রভাব পড়ত না তার উপর। এজন্য প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক চাপ। সেটাও দেয়া হল ভালো করে। চন্দ্র-দর্শীর জীবনে এমন কিছু পরিবর্তন এসেছে যা সে কোনোকালে ধরতে পারবে না। ওর একেবারে সরল মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে, প্রতিটি অনুতে এসেছে নতুন মোড়, নতুন বাঁক। ও বেঁচে গেলে সেসব গঠন হয়ে উঠবে চিরঞ্জীব। কারণ তার জিনগুলো এসব বয়ে চলবে প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে; শতাব্দী-সহস্রাব্দান্তরে।
এ এক ধীর, জটিল প্রক্রিয়া। কিন্তু ক্রিস্টাল মনোলিথের যথেষ্ট ধৈর্য আছে। সে বা তার আর সব জমজেরা শুধু আধা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েই ক্ষান্ত হয়নি, যেখানে যত প্রাণী পাচ্ছে তার সব নিয়েই করে চলেছে নিরীক্ষা। মরিয়া হয়ে কাজ করছে সাফল্যের আশায়। শত ব্যর্থতায়ও কিছু যায় আসে না-একটা, মাত্র একটা সাফল্য উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে চারদিক। বদলে দিতে পারে পৃথিবীর রীতি।
পরের নতুন চাঁদ আসতে আসতে তারা একটা জন্ম আর দুটো মৃত্যু দেখতে পায় চোখের সামনে। একটা মরেছে ক্ষুৎপিপাসায়, অন্যটা রাতে ফেরার সময়। দু খণ্ড পাথরকে ঠুকে দেয়ার কষ্টসাধ্য কাজটা করার সময় সেই বনমানব নিজের মাথাকেই গুঁড়িয়ে দেয়। সাথে সাথে আঁধার ঘনিয়ে আসে মনোলিথ জুড়ে আর গোত্রটাকে জাদুমুক্ত করা হয়। কিন্তু পড়ে যাওয়া বন মানুষটা আর উঠে দাঁড়ায়নি এবং অবশ্যই, সকালে সেখানে কিছুই ছিল না।
পরের রাতে আর কোনো কাজই হয়নি। ক্রিস্টাল তখনো নিজের ভুল বিশ্লেষণে মত্ত। রাত্রি নামার সাথে সাথে ধীরেসুস্থে গোত্রটা ফিরে যায় আশ্রয়ে। এখনো মনোলিথের উপস্থিতি তাদের কাছে অর্থহীন। পরের রাতে জিনিসটা আবারো তাদের জন্য তৈরি হয়ে নেয়।
সেই চার সুখী বনমানুষের সাথে এবার যুক্ত হয়েছে অসাধারণ সব কাজ। চন্দ্র-দর্শী কাঁপতে থাকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। যেন পুরো মাথাটা ফেটে বেরিয়ে পড়বে। প্রাণপণে চেষ্টা করে চোখদুটো খুঁজে নিতে। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর মানসিক যাতনা তার শক্ত থাবায় একবিন্দু ঢিল দেবে না। নিজের সবটুকু চেতনা এর বিরুদ্ধে কাজ করলেও সে শিক্ষাটা শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিতে বাধ্য হল।
চিন্তাটা তার বংশধরদের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। পথের চারধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে কত কত খাদ্য! সময় বদলে গেছে। অতীতের জ্ঞানের বংশানুক্রমিক পরিবহনের এই শুরু। অরণ্যচারী মানবদলকে এর সাথে অবশ্যই মানিয়ে নিতে হবে, নয়তো মিশে যেতে হবে ধূলিকণার সাথে। সেসব বিশালাকার শ্বাপদের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যাদের হাড়গুলোই শুধু চুনাপাথুরে পাহাড়ে পাহাড়ে ফসিল হয়ে আটকে আছে।
চন্দ্র-দর্শী স্থির চোখে চেয়ে থাকে ক্রিস্টাল মনোলিথের দিকে। এদিকে তার মস্তিষ্কের সবটাই খুলে খুলে যায় এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামনে। কখনো কখনো অনুভব করে অমিত তেজের বিপ্লব। কিন্তু সব সময় তার অনুভূতির প্রায় সবটা জুড়ে বসত করে ক্ষুধার দানবেরা। আর ধীরে ধীরে তার অজান্তেই হাতের মুঠোগুলো ভাজ হয়ে যায়, যায় খুলে। এক অভিনব পথে কাজটা হয়। এমন এক পথে, যেটা জীবনের বাকীটাকে তুলে ধরতে পারে আয়েশী, আলতো হাতে।
.
বুনো শূকরের পিল মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছিল, চলছিল ট্রেইল ধরে। হঠাৎ করেই চন্দ্র-দর্শী দাঁড়িয়ে যায়। শূকর আর বনমানুষের দল সব সময়ই একে অন্যকে হেলা করে এসেছে, কারণ এদের মধ্যে মোটেও দ্বন্দ্ব নেই। ভদ্র জন্তু-জানোয়ারের মতো নিজের নিজের পথে চলে, কারণ অপরের সাথে খাবার নিয়ে টানা-হেচড়া নেই।
এখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চন্দ্র-দর্শী; ইতস্তত করছে। মন চলে যাচ্ছে সামনে পেছনে, শরীরও যাচ্ছে হেলে। যেন সে এসব ইচ্ছা করে করছে না। তারপর, যেন স্বপ্নের ঘোরেই তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় মৃত্তিকার কঠিন বুকের দিকে। ঠিক কীসের জন্য এই খোঁজাখুঁজি সেটা সে আদৌ বলতে পারবে না-যদি জবান খুলে যায়, তাও না। পাওয়ার পরই চিনতে পারল সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে।
ইঞ্চি ছয়েক লম্বা তীক্ষাগ্র এক ভারি পাথর সেটা। হাতে ঠিকমতো বসানো যাচ্ছে না, তবু এতেই চলবে। সে জিনিসটাসহ হাত ঘোরায় মাথার উপরে, নিচে। এর বাড়তি ওজনটাও কেমন মাদকতা এনে দেয়। প্রথমবারের মতো ক্ষমতা আর প্রাতিষ্ঠানিকতার শক্তিমান ভূত ভর করে তার উপর। সে সবচে কাছের শূকর ছানাটার দিকে চলতে শুরু করল উৎসাহের সাথে।
শূকর দলের নিচু স্তরের বুদ্ধিমত্তার হিসেবেও এ এক বোকাটে কমবয়েসি জানোয়ার। চোখের কোণা দিয়ে চন্দ্র-দর্শীর এগিয়ে আসাটা ঠিকই দেখতে পায় কিন্তু পাত্তা দেয় না মোটেও। আমলে নিয়েছে তখনি যখন আর সময় নেই। আসলেইতো, কেন ছানাটা এই নিতান্ত গোবেচারা প্রাণীগুলোকে গোনায় ধরবে? সে বেখেয়ালে ঘাসের গোড়া চিবিয়েই চলল যে পর্যন্ত চন্দ্র-দর্শীর প্রস্তরখণ্ডটা তার নিষ্প্রভ সচেতনতাকে সচকিত করে না তোলে। হত্যাকাণ্ডটা এত নীরবে, এতো দ্রুত ঘটে গেল যে বাকীরা নিজেদের সামনের ঘাস থেকে মুখও তুলল না।
দলের বাকী অরণ্য-মানবেরাও অবাক চোখে কান্ডকারখানা দেখে। জুটে যায় চন্দ্র-দর্শীর আশপাশে। আরেকজন তুলে নেয় রক্তপাতের আরেক অস্ত্র। আঘাতে আঘাতে বিক্ষত করে দিতে থাকে মরা জটাকে। এরপর বাকীরা কাঠি বা পাথর যাই পাক না কেন, যুগিয়ে নিয়ে নেমে পড়ে সোৎসাহে। থেতলে থেতলে ভর্তা করে ফেলেছে মাংসের তালটাকে।
এবার একটু বিরক্তি আসে। কী লাভ এ অকাজে! দু-চারজন আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইচ্ছামতো, কেউ আবার ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়েছে অবোধ্য জিনিসটার সামনে।
তারা জানেও না জগতের ভবিষ্যৎ ওদের সিদ্ধান্তের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে উদগ্রভাবে।
অনেক অনেক সময় কেটে যাবার পর কোনো এক পেটের জ্বালায় কাতর বনমানুষী নিজের পাথরের উপর লেগে থাকা সামান্য থেতলে যাওয়া মাংসের দিকে অপলক তাকায়। দু-হাতের পাতায় মেলে ধরা তার অস্ত্রটা।
একটু, সামান্য একটু চেটে দেখে সে মাংসটুকু।
আরো অনেক অনেক সময় লেগে যায় চন্দ্র-দর্শরি। অবাক, বিহ্বল, চিত্রার্পিত বিস্ময়ে সে নিজের ভিতরে উপলব্ধি করে আর কখনো ক্ষুধা তাকে অহর্নিশি জ্বালাবে না।
অধ্যায় ৪. চিতা
ওদের পরিকল্পনার অস্ত্রগুলো অনেক বেশি সরল। তবু এ দিয়েই তারা পুরো পৃথিবীর কর্তৃত্ব নিয়ে নিতে পারে, বনমানুষদের করে তুলতে পারে জগতের অধীশ্বর। পাথর ধরা হাতই সবচে পুরনো অস্ত্র। এ হাত যে কোনো ধাক্কার শক্তিকে আশ্চর্যজনকভাবে ঐশিতা দিতে পারে। অনন্তর এলো হাড়ের ব্যবহার। এগুলো যে কোনো মত্ত দাতাল আর নখরওয়ালা প্রাণীর বিরুদ্ধে চমকপ্রদ কাজ দেয়। এসব অস্ত্রের সাহায্যেই সামনের অসীম-ছোঁয়া চারণভূমির অযুত-নিযুত প্রাণী হয়ে পড়ে তাদের খাদ্য।
অথচ ওদের আরো কিছু থাকা জরুরী। কারণ ওদের দাঁত আর নখ আজো ইঁদুরের চেয়ে বড় কোনোকিছু গ্রহণে সম্মত নয়। কপাল ভালো, এতদিনে হিসেবি প্রকৃতি ঠিক ঠিক অস্ত্রে ওদের সাজিয়ে দিয়েছেন। অস্ত্রের নাম বুদ্ধিমত্তা।
প্রথম প্রথম খুবই ভোতা-টোতা ছুরি-করাতে কাজ চলত। এমন এক চেহারার যন্ত্র এগুলো যা আগামী ত্রিশ লক্ষ বছর এক-আধটু বদলে গিয়ে চালাতে থাকবে কাজ। কোনো কোনো কাজ অ্যান্টিলোপের নিচের চোয়ালের দাঁতাল হাড় দিয়েই চলে। লৌহযুগের আগে তারা আর তেমন বড়সড় ধাপ পেরুবে না। ছোট হরিণের শিং দিয়ে ছুরির কাছাকাছি সুবিধা লুটে নেয়া যায়। ছোটখাট যে কোনো জন্তুর পুরো চোয়াল দিয়ে আঁচড় কাটতো তারা।
পাথুরে লাঠি, দন্তময় করাত, শিঙের ছোরা আর হাড়ের আঁচড়ানিই তাদের প্রয়োজনীয় অসাধারণ আবিষ্কার। অস্তিত্বের জন্য এরচে বেশি কিছুর চাহিদা নেই। শিঘ্রি বনমানবেরা সেসব হাতিয়ারের সবটুকু ক্ষমতার কদর বুঝবে। কিন্তু তাদের জড়ভরত আঙুলগুলোর সেসব ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন করতে বা ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করতেই বহু মাস যাবে পেরিয়ে।
সময় দিলে হয়তো তারা নিজে থেকেই এমন প্রায় অবাস্তব কষ্টসাধ্য ধারণা পেত। প্রাকৃতিক সব জিনিসকে হয়তো ব্যবহার করত কৃত্রিম অস্ত্র হিসেবে। কিন্তু বৈরী পরিবেশ সব সময় চতুর্দিক থেকে মুখ ব্যাদান করে থাকে। আর আজো তাদের সামনে ব্যর্থতার হাজার দুয়ার খোলা।
অরণ্য মানবকুলকে প্রথম সুযোগ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টা কখনোই আসবে না। ভবিষ্যৎটা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই তাদের হাতে। শুধু হাতের উপর নির্ভরশীল।
.
চাঁদের কলা বদলে বদলে যায়। শিশুরা জন্মে, বেঁচে-বর্তে যায় প্রায়ই। ত্রিশ বছরের অথর্ব, দন্তহীন বুড়োরা যায় মরে।। চিতা ঠিকই রাতে রাতে নিজের খাজনাটুকু কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে চলে। আজো নালার ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে চলে অন্যেরা। আর উন্নয়ন এগিয়ে চলে গোত্রে। একটু একটু করে। এক বছরের ফারাকে চন্দ্র-দর্শী আর ওর উপজাতিটাকে একদম চেনাই যায় না।
নিজের শিক্ষাটুকু ঠিকই নিয়েছে তারা। আজ তারা সামনে পড়া সব টুকটাক যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ক্ষুৎপিপাসার সেই দুঃসহ স্মৃতি বিলীয়মান। কমে আসছে শুকর জাতীয় প্রাণীগুলো। তাতে কী, ছোট হরিণ, অ্যান্টিলোপ আর. জেব্রা আছে সমভূমি জুড়ে। হাজার হাজার। এইসব প্রাণী এবং বাকীরাও পড়েছে মহা ফাঁপড়ে; তারা সবাই শিক্ষার্থী শিকারীদের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে সময়ের প্রবাহে।
আজ আর তারা প্রাণ-ক্ষুধার টানাপোডনে পড়ে আধমরা নয়। আলসেমির জন্য পড়ে আছে বিস্তর সময়। সময় পড়ে থাকে ভাবনার আদি সূত্রগুলোর জন্য। ভাবনা! ভাবনার জন্য প্রয়োজন শুধু এই সময়টুকুই। নতুন জীবনযাত্রা বেশ উষ্ণভাবেই বরণ করেছে তারা। এ নবজন্মের সাথে কোনোভাবেই মনোলিথের সম্পর্ক খুঁজে পায়নি। মনোলিথটা আজো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে প্রসবণের পথে। এমনকি কখনো তারা মনোলিথের দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারটা বোঝার জন্য একটু থমকে দাঁড়ালেও নিশ্চয়ই মনে করত তাদের এ উন্নতিটা পুরোপুরি নিজস্ব। কারণ এরই মধ্যে জীবনের আর সব রূছু চিত্র মুছে গেছে মন থেকে।
কিন্তু কোনো ইউটোপিয়াই[৭] নিখুঁত নয়। এ স্বর্গরাজ্যেরও দু-ত্রুটি ছিল। প্রথমটা হলো খোঁজাখুঁজিতে মত্ত চিতা। চিতাটার বনমানুষ-পিপাসা আরো বেড়েছে ওদের শরীর তাগড়া হওয়ার সাথে সাথে। অন্য ত্রুটিটা হল খালের ওপারের গোত্র। কীভাবে যেন ওরা আজো টিকে আছে ধুঁকে ধুঁকে। এখনো গোঁয়ার গোবিন্দের মতো খেয়ে মরতে নারাজ।
হঠাৎ করেই চিতা সমস্যার সমাধান হাজির হয়ে গেল। একটা বড়সড়-বলা চলে প্রাণঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল চন্দ্র-দর্শীর দল। প্রথমবার ধারণাটা মনে আসার সাথে সাথে সে বেশ আনন্দের সাথে উদ্বাহু নৃত্য করেছিল, আর এ অবস্থায় সবদিক বিবেচনায় না নেয়ার দোষও তাকে দেয়া যায় না।
এখনো কালেভদ্রে দুর্দিনের মুখোমুখি হয় বুনোরা। কিন্তু তা আর অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দেয় না। গোধূলী পর্যন্ত একটা শিকারও করতে পারেনি; এখনি চোখে পড়ে গিরিগর্তের ঘরবাড়ি। চন্দ্র-দর্শী নিজের ক্লান্ত আর হতাশ দলটাকে টেনে চলে আশ্রয়ের দিকে। ঠিক এমন সময় চোখে পড়ে যায় প্রকৃতির সবচে দুর্লভ এক উপহার।
একটা পূর্ণবয়স্ক অ্যান্টিলোপ পথের ধারে পড়েছিল। সামনের পা ভাঙা। কিন্তু লড়ার মতো যথেষ্ট শক্তি ছিল বলেই চারধার থেকে ঘিরে ধরা খেকশিয়ালের দল তার তলোয়ারের মতো শিংগুলোর প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করে চলেছে। রাতের শিকারীদের ধৈর্য ধরার মতো সময় সুযোগ আছে। তারা জানে, শুধু সময় ব্যয় করতে হবে, ব্যস।
কিন্তু শেয়ালের দল প্রতিযোগিতার কথা বেমালুম ভুলে বসেছে। বনমানুষের দল এগিয়ে এলে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করে। আতঙ্ক জাগানিয়া শিংগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে বুনোরাও সাবধানে, ভয়ে ভয়ে চারদিক থেকে একটা বৃত্ত গড়ে চলে। এরপর এগিয়ে যায় পাথরখণ্ড আর লাঠিসোটা নিয়ে।
আক্রমণ খুব বেশি সমন্বিত বা ফলদায়ক হল না। তাই জটা হাল ছেড়ে দিতে দিতে পুরোপুরি রাত নেমে যায়। খেঁকশিয়ালের দল ফিরে পাচ্ছে আত্মবিশ্বাস। পেটের জ্বালা আর ভয়ে কাবু হয়ে চন্দ্র-দর্শী অকস্মাৎ উপলব্ধি করে যে এসব কষ্ট একেবারে বৃথা যেতে বসেছে। আর এখানে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়।
চন্দ্র-দর্শী এবার নিজেকে এক তীক্ষ্ণবুদ্ধির মেধাবী হিসেবে প্রমাণ করে বসে; আগেও অনেকবার করেছে, পরেও করবে। কল্পনার কত কষ্টের সব ধাপ বেয়ে বেয়ে সে হঠাৎই সুখস্বপ্ন সুধার দেখা পায়। অ্যান্টিলোপের মরদেহটা শুয়ে আছে-তার নিজের নিরাপদতম গুহার ভিতরে! সাথে সাথে শরীরটাকে টানতে শুরু করে গুহামুখের দিকে। বাকীদের উদ্দেশ্য বুঝতে বাকী থাকে না। একটু পরে হাত লাগায় তারাও।
সে কাজটার কষ্ট সম্পর্কে জানলে কখনোই একাজে নামতে না। শুধু তার দারুণ শক্তি আর পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া গোঁড়ামি দিয়ে গুহার ঢাল ধরে উপরদিকে টেনে চলে মরা জিনিসটাকে। হতাশায় কেঁদে দিয়ে কতবার ছেড়েছুঁড়ে দিল পুরস্কারটাকে, কতবার মনের গভীর থেকে আসা ইচ্ছাশক্তি নিয়ে ক্ষুধার তাড়নায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আবার কখনো বাকীরা সাহায্যের হাত বাড়ায়, কখনো হাত নেয় গুটিয়ে। অবশেষে কাজটা সমাধা হয়, গুহার ঠোঁট পেরিয়ে মরা জানোয়ারটাকে তুলে আনা হয় ভিতরে। সূর্যালোকের প্রথম ক্ষীণ রশ্মি হারিয়ে যাবার পর ভোজ শুরু হল। . কয়েক ঘণ্টা পরে একটু শব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে ওঠে চন্দ্র-দর্শী। কেন যেন চারপাশের সাথীদের ঘুমন্ত দেহ ছাড়িয়ে তার কান পেতে দেয় আরো দূরে।
চারপাশের ভারি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। সারাটা ভুবন যেন ঘুমন্ত। ঠিক মাথার উপর থেকে উপচেপড়া চন্দ্রালোকে গুহার সামনের পাথরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। যে কোনো বিপদের ভাবনাই অবান্তর।
এবার অনেকদূর থেকেই যেন একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ এগিয়ে আসে। চন্দ্র-দর্শী হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, উঁকিঝুঁকি দিল গুহাচত্বরে দাঁড়িয়ে।
নিজের ডানে সে এমন কিছু দেখতে পায় যা বেশ কয়েক মুহূর্ত জুড়ে একেবারে অসাড় করে রাখে তাকে। মাত্র বিশ ফুট নিচেই দুটি ভাটার মতো জ্বলন্ত চোখ তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। চিতাটা ঐ গন্ধের ইন্দ্রজালে এত বেশি ফেঁসে গেছে যে পেছনে পাথরের উপর ঘুমন্ত নরম দেহগুলোর কথা ভুলেই যায় একদম। এর আগে বাঘটা কখনোই এত উপরে উঠে আসেনি। নিচের দিকের গুহাগুলোকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেই এগিয়ে আসে, যদিও সেসব গিরিগর্তের বাসিন্দাদের ব্যাপারে সে পূর্ণ সজাগ। এবার ও অন্য ক্রীড়ায় মত্ত। রক্তের ক্ষীণধারা জোছনায় ধুয়ে ধুয়ে নেমে আসছে নিচে।
মুহূর্ত কয়েক পরেই উপরের দিকের গুহাবাসীদের চিৎকারে রাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে যায়। চমক দেয়ার সুযোগ চলে যাওয়ায় চিতাটা হৃষ্টচিত্তে রক্তহিমকরা এক হুংকার দিল। কিন্তু আগপাশ ভালো করে দেখে নেয়নি-কারণ সে জানে ভয়ের কিছু নেই।
রিজের উপর উঠে এসে খোলা সরু জায়গায় এক মুহূর্তের জন্য দম নেয় সে। চারদিকে শোণিতের ঘ্রাণ মোটা মাথাটাকে উন্মত্ত করে তুলেছে। ভরিয়ে তুলেছে অতি আকাক্ষায়। একবিন্দু দ্বিধা না করে আলতো পায়ে প্রবেশ করে গুহায়।
এটাই চিতার প্রথম ভুল। জোছনা থেকে ভিতরে ঢুকেই ধাঁধায় পড়ে যায় এর রাতের অতি উপযোগী চোখদুটোও। বুনোদলটা চাঁদের আলোর চিত্রপটে বাঘটার অবয়ব দেখতে পায় স্পষ্ট। কিন্তু স্পষ্টভাবে চিতা ওদের দেখতে পায়নি। তারা ভয়ে অস্থির হলেও আজ আর অসহায় নয়।
নিজের লেজটা অতি আত্মবিশ্বাসে এদিকসেদিক নাড়াতে নাড়াতে চিতাবাঘটা নিজের লোভনীয় খাদ্যের খোঁজে একেবারে ভিতরে প্রবেশ করে বসেছে। খোলা প্রান্তরে শিকারের মুখোমুখি হলে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু এখন একদল বনমানুষ ফাঁদে পড়ে গেছে, ধ্বংসের ভয়ই তাদের অসম্ভব কাজের পথ বাৎলে দেয়। প্রথমবারের মতো তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার সুযোগ পেয়েছে।
প্রথমে মাথায় আঘাত পেয়ে চিতাটা বুঝতে পারে কোথাও বড় ধরনের গড়বড় আছে। সেটা যে কোথায় তা খুঁজে পায় না। নিজের নখর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে গেঁথে ফেলে নরম মাংসে, একই সাথে আরো ব্যথা টের পায়। পেটের দিকে বেশ তীক্ষ্ণ, কেটে ফেলার মতো শক্তিশালী আঘাতের স্বাদ টের পায় একবার, দুবার, এমনকি তৃতীয়বারও। একপাক ঘুরে যায় হিংস্র জন্তুটা, চারপাশের নৃত্যরত ভয় পাওয়া প্রাণীগুলোকে প্রতিরোধ করতে চায়।
এবারো আরেক কষ্ট টের পায় সেটা। কেউ যেন নাকটা একদম কেটে ফেলেছে। ওর সাদা দাঁতগুলো ঝিকিয়ে ওঠে, বসে যায় সামনের অন্টিলোপ হাড়গোড়ের উপর। এবার অবিশ্বাস্যভাবেই কাটা পড়ে তার লেজটা।
চারদিকে পাক খাচ্ছে জটা। গুহা দেয়ালের গায়ে অন্ধভাবেই আঘাতের পর আঘাত করছে। এতক্ষণ যাই করে থাক না কেন, আঘাত বর্ষণ থেকে একটুও বিরত হয়নি বনমানুষেরা। ওদের হাতে নিষ্ঠুর সব যন্ত্র, হাত অপরিণত হলেই বা কী এসে যায়, শক্তি আছে অপরিমেয়। এদিকে চিতার নাক ব্যথা চূড়ান্তে পৌঁছেছে, আতঙ্কে পাগল হওয়ার দশা। অবিসংবাদিত শিকারীই এবার পরিণত হয়েছে অসহায় শিকারে, সব চিন্তা বাদ দিয়ে পিছু হটার ভাবনায় সে এখন দিশেহারা।
এবার বাঘ দ্বিতীয় ভুলটা করে বসে, ব্যথা-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কোথায় আছে তাই ভুলে বসে। নয়তো চোখদুটোও গেছে নষ্ট হয়ে। ব্যাপার যাই হোক না কেন, বজ্রের মতো ছিটকে বেরোয় গুহা থেকে। খোলা বাতাসে পড়তে পড়তে বিকট গর্জনও করে চিতাটা। অনেক যুগ পরে যেন পতনের এক ভারি আওয়াজ উঠে এলো। প্রাণীটা পাহাড়ের অর্ধেক পেরিয়ে নিচে পড়ে গেছে। পরে শুধু ছোটখাট পাথরের গড়িয়ে পড়ার শব্দই শোনা যায়। পাথরগুলো হারিয়ে যাচ্ছে আঁধার রাতের পথে।
আনন্দের আতিশয্যে অনেকক্ষণ ধরে চন্দ্র-দর্শী নেচেকুদে বেড়ায় গুহামুখে। অকস্মাৎ যেন টের পায়, আর সে শিকার নয়, নিজেই শিকারী।
গুহায় ফিরে গিয়ে জীবনে প্রথমবারের মতো বেঘোরে ঘুমায় অরণ্যচারী প্রাচীন মানব।
.
তারা সকালে পাহাড়ের পাদদেশে দেখতে পায় চিতার শরীরটাকে। সবাই জানে, এ এক মৃত শরীর-আর কিছু নয়। তবু বিকৃত দানবটার আশপাশে সহজে কেউ ঘেঁষতে চায় না। কিন্তু এবার ওরা এগিয়ে এসেছে হাড়ের ঘুরি আর আঁচড় কাটার হাতিয়ার নিয়ে।
কাজটা আসলেই কঠিন। সেদিন আর বনমানুষের দল চষে বেড়ায়নি পাহাড়ের পাদদেশ। প্রথমবারের মতো।
অধ্যায় ৫. ভোরের প্রথম মোকাবিলা
ভোরের প্রথম মৃদু আলোয় দলকে পানির দিকে ঠেলে দিয়েই চন্দ্র-দর্শী হঠাৎ করে থেমে গেল পথের উপর। কিছু একটা নেই। কী যে নেই, বোঝা যাচ্ছে না-কিন্তু কিছু একটা নেই। এ নিয়ে চিন্তা ক্ষয়ের কোনো কারণ দেখে না সে, কারণ সকাল থেকে তার মাথায় চক্কর দিচ্ছে অন্য ধান্ধা।
বিজলীর মতো, মেঘের কালো দলের মতো, চাঁদের সরু আর পেটমোটা হওয়ার মতো সেই বিশাল মনোলিথটা উধাও হয়ে গেছে। যেভাবে এসেছিল, চলে গেছে সেভাবেই। একবার আঁধার অতীতে চলে যাওয়ায় আর কখনোই চিন্তাটা জ্বালাতন করবে না চন্দ্র-দর্শীর মনকে।
সে কোনোকালেই জানবে না কী হারিয়ে গেল চিরতরে। কী করে দিয়ে গেল ওর পুরো জগৎটায়। চন্দ্র-দর্শীর সাথীরা থমকে দাঁড়ায়নি। সকালের রহস্যময় কুয়াশায় তারা শুধু ঘিরে ধরেছে দলপতিকে, কেন দাঁড়িয়ে আছে ও এখানে?
নালাটার নিজেদের দিকের প্রান্তে নিজেদের ত্রাসহীন এলাকায় দাঁড়িয়ে অন্যেরা চন্দ্র-দর্শী আর তার দলের দশ বারোজন পুরুষের দেখা পায়। যেন প্রথম আলোয় চলন্ত কোনো বহর। সাথে সাথেই নিজেদের প্রাত্যহিক চ্যালেঞ্জ শুরু করে দেয়। এই প্রথম সেপাশ থেকে কোনো জবাব আসে না।
ধীরে সুস্থে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সবচে বড় কথা, নিরবে-চন্দ্র-দর্শী আর ওর দল নদীর অন্যধারের নিচু টিলাটায় গিয়ে ওঠে। ওদের এসব কাণ্ডকারখানা দেখে অন্যেরা একদম নিশুপ হয়ে গেল। বাহাদুরির বদলে হঠাৎ আসা ভয় ওদের জড়সড় করে ফেলেছে। ওরা হালকা বুঝতে পারে যে কিছু একটা ঘটছে, কী যে ঘটছে সেটা বুঝতে পারে না। এবারের মুখোমুখি হওয়াটা আর সব বারের চেয়ে ভিন্নতর। চন্দ্র-দর্শীর দলের হাড়ি-লাঠি আর চাকু-ছুরি ওদের মোটেও ভয় পাওয়ায়নি, কারণ উদ্দেশ্যের এক কোণাও অন্যদের উপলব্ধিতে ঠাই পায়নি। অন্যরা শুধু বুঝতে পেরেছে যে তাদের শত্রুদলের নড়াচড়ায় ভিন্ন কিছু বোঝা যায়।
পানির প্রান্তে পার্টিটা শেষ হতেই অন্যদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। নেতৃত্ব দিচ্ছে এক কানওয়ালা, তারা আবার আধাআধি আত্নবিশ্বাস ফিরে পেতে থাকে। এই বিশ্বাসটা তুঙ্গে থাকে মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরই লা জওয়াব হয়ে যায় তারা একটা দৃশ্য দেখে।
চন্দ্র-দর্শী নিজের হাতটাকে অনেক অনেক উপরে তুলে ধরার চেষ্টা করে। দেখিয়ে দিচ্ছে দলের লম্বা লোমে আবৃত শরীরগুলোর পেছনে এতক্ষণ লুকিয়ে রাখা বিশেষ একটা গর্বের জিনিসকে। ও একটা ডাল ধরে রেখেছে, সেটার উপর চিতার রক্তাক্ত মাথা। একটা কাঠি ঢুকিয়ে মুখটাকেও হাঁ করিয়েছে ওরা। সামনের দিকের লম্বা দন্তগুলো ঝিকিয়ে উঠেছে সূর্যোদয়ের আলোর স্রোতে।
অন্যদের বেশিরভাগই এত বেশি ভয় পেয়েছে যে বাহতের মতো চেয়ে আছে মাথাটার দিকে। কোনো কোনোটা ধীরে পিছু হটছে। চন্দ্র-দর্শীর এরচেয়ে বেশি উৎসাহের দরকার নেই। মাথার উপর বিকৃত জিনিসটা ধরে রেখেই সে ক্ষীণস্রোতা খালটা পেরুতে শুরু করে। একপল দ্বিধা করে পিছু নেয় সঙ্গীরাও।
দূরপ্রান্তে পৌঁছার পরও এক কানওয়ালা নিজের জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে রইল। হয় সে অতি সাহসী, নয়তো নিতান্তই নির্বোধ। সম্ভবত বুঝতেই পারেনি এ অসম্ভব কী করে সম্ভব হয়! বীর হোক আর ভীতু, শেষে কোনোটাই কাজ দেয় না। কারণ এবার অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু নেমে এসেছে তার মাথায়।
ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে অন্যেরা আশপাশের ঝোপে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু একসময় তারা ঠিকই ফিরে আসবে, ঠিকই ভুলে যাবে গোত্রপতিকে।
কয়েক পল চন্দ্র-দর্শী তার নিজের নতুন শিকারের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। অবাক চোখে দেখে মরা চিতাবাঘটারও হত্যার ক্ষমতা আছে।
আজ সে জগদীশ্বর হলেও ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কী করতে হবে এরপর।
কিন্তু সে হয়তো কিছু না কিছু করার কথা ভেবে রেখেছে।
অধ্যায় ৬. মানুষের অরুণোদয়
নতুন এক প্রাণী জন্মেছে গ্রহে। আফ্রিকার উৎসভূমি থেকে উঠে এসে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে ছড়িয়ে পড়াটা এত মন্থর গতির যে সাগর আর ভূমিতে বিচরণশীল প্রাণীর উপরে একটা ভালো আদমশুমারীতে হারটাকে গোনা গুনতিতেই ধরা হবে না। এখনো তেমন জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় না যার উপর ভিত্তি করে বলা যায় এরা উন্নয়ন করবে। বাঁচবে যে তাই জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ এ বসুধার বুকে অগুনতি দানব প্রাণী ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। তাদের পাল্লা আজো একবার এদিকে, আরেকবার সেদিকে হেলে যায়।
স্ফটিকগুলো আফ্রিকায় বর্ষিত হওয়ার লাখো বছরের মধ্যে বনমানুষেরা কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু তারা বদলে যাচ্ছে। তারা এমন কিছু দক্ষতা অর্জন করেছে যা আর কোনো প্রাণীর নেই। হাড়ের তৈরি লাঠিগুলো বাড়িয়ে তুলেছে সম্পদ, বাড়িয়ে চলেছে তাদের শক্তি। আজ আর প্রতিযোগী খাদকদের সামনে তারা অসহায় নয়। ছোটখাট মাংশাসীগুলোকে নিজেরাই তাড়িয়ে বেড়াতে পারে; বড়গুলোর উৎসাহে বরফ ঢেলে দিতে পারে, মাঝে মাঝে করে লড়াই।
তাদের বিকট দর্শন দন্তসারি ছোট হতে থাকে; আজ আর সেসব জরুরী নয়। তীক্ষ্ণ কোণার পাথর দিয়ে শিকড়বাকড় খুঁড়ে নেয়া যায়, কাটা যায় গোশত আর আঁশ। এগুলোই বড় দাঁতের জায়গা দখল করে কালক্রমে। বুনোরা আর দাঁত হারালে বা দাঁতের সমস্যায় পড়লে উপোস দেয় না। এসব সরলতম ভোতা হাতিয়ার মানিয়ে নিতেই তাদের পেরিয়ে যায় কত শতাব্দী! শক্তিশালী জান্তব চোয়াল নিচু আর ছোট হয়ে আসে। গালের হাড় আর বেরিয়ে থাকে না, তাই মুখ আরো স্পষ্ট, কোমল, জটিল আওয়াজ তুলতে পারে নির্বিঘ্নে। ভাষা আজো সুদূর পরাহত; লাখো শতাব্দী পেছনে পড়ে আছে-কিন্তু এর দিকে প্রথম কদম ফেলা হয়ে গেছে।
এবার ভুবন বদলে যেতে লাগল। দুনিয়ার সর্বত্র করাল ছোবল হেনে ফিরে গেল হিমযুগ। এর চার চারটা জোয়ার দু-লাখ বছর করে সময় নিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে গেল পুরো বিশ্বটাকে। ভাটার সময়টুকু বাদ দিয়ে হিমবাহের বহর নির্দয়ভাবে হত্যা করল কত অপরিণত প্রাণীকে! চারদিকে সেসব প্রাণীর চিহ্ন। তারা পারেনি মানিয়ে নিতে।
কুম্ভকর্ণের তামসিক নিদ্রা শেষ হলে বনমানুষসহ গ্রহের প্রথমদিকের জীবনগুলো টিকে যায়। কেউ বংশধর ছেড়ে যায় পৃথিবীর বুকে, তারা হারিয়ে না গেলেও বদলে গেছে অনেকটা। এবার হাতিয়ারের কারিগরেরা হাতিয়ারের প্রয়োজনেই বদলে গেছে।
হাড়ি আর পাথরের ব্যবহারের জন্য তাদের হাত নিয়েছে নতুন রূপ, যেটা প্রাণীরাজ্যের কোথাও পাওয়া যাবে না। এ হাতই আবার নতুন, জটিল হাতিয়ার গড়ার উপযোগী হয়ে ওঠে, সেসব নতুনতর যন্ত্রপাতির প্রয়োজনে বদলে যায় তাদের মস্তিষ্ক, নব রূপলাভ করে বাহ্যিক অঙ্গগুলো। এ এক দ্রুতিময়, বাড়ন্ত প্রক্রিয়া; এর শেষ পরিণতিকেই ডাকা হয় মানব নামে।
প্রথম সত্যিকারের মানব যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করত তা তার পূর্বপুরুষের ব্যবহার করা জিনিসের চেয়ে খুব একটা ব্যতিক্রমী কিছু নয়; কিন্তু সে সেগুলোকে অনেক সহজে অনেক বেশি কাজে ব্যবহার করতে শেখে। সেসব যন্ত্রপাতিও শতাব্দীর অতলে কী করে যেন হারিয়ে যায় সর্বকালের সবচে জরুরী ব্যাপারটার উদ্ভবের আগ দিয়ে। একে ধরাও যায় না, যায় না ছোঁয়া। কথা বলতে শিখতেই সে সময়ের উপর প্রথম বিজয়মাল্যটা ছিনিয়ে আনে নিষ্ঠুরতার সাথে। এবার জ্ঞানকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পরিবাহিত করে চলে সহজেই। আগের প্রজন্মের অভিজ্ঞতার পুরোটাই চলে আসে পরের প্রজন্মের হাতের মুঠোয়।
জন্তু জানোয়ারের আছে শুধু বর্তমান, কিন্তু মানুষ এবার অতীতসমৃদ্ধ প্রাণী, তার আছে স্বপ্নেছাওয়া ভবিষ্যৎ।
এবার সে জোরেসোরে প্রকৃতিকে বেঁধে ফেলতে চায় অগ্নিদেবের বাহুডোরে। সে আগুনের সাথে সাথে আবিষ্কার করেছে প্রযুক্তির স্বর্ণদুয়ার, নিজের জান্তব অতীতকে ফেলে দিয়েছে যোজন যোজন পেছনে।
প্রস্তর হার মেনে যায় তাম্রযুগের কাছে, তামা মাথা নোয়ায় লৌহ শৃঙ্খলের সামনে। শিকারের শেষ পরিণতি হিসেবে জন্ম নেয় কৃষি। গোত্রগুলো একত্র হয় গ্রামে, গ্রামের শেষ পরিণতি শহর। কথা চিরস্থায়ী রূপ নেয়; অবদান রাখে লম্বা পাথর, কাদার ফলক আর প্যাপিরাস। আজকাল সে আবিষ্কার করেছে দর্শন শাস্ত্র আর ধর্ম। এবার বসত করা শুরু করেছে আকাশে, পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেনি, আজো জয় করতে পারেনি দেবতাদের।
তার শরীর আরো প্রতিরক্ষাহীন হয়ে পড়ার সাথে সাথে শত্রুরাও বেশি বেশি ভীত হয়ে পড়ে। স্টোন আর ব্রোঞ্জ আর আয়রন আর স্টিলের কাল আসার সাথে সাথে সে প্রতিটা জিনিসকে পরখ করে দেখেছে, যা ভাঙা যায়, যা চিরে দেখা যায় এমন সব কিছুকেই। কিছুদিনের মধ্যেই শত্রুকে দূর থেকে ঘায়েল করার কূটবুদ্ধিও তার দখলে চলে আসে। তীর, ধনুক, বন্দুক আর সবশেষে গাইডেড মিসাইল” তাকে দিয়েছে অসীম পাল্লা, দিয়েছে আর সব; শুধু দেয়নি অসীম ক্ষমতা।
মাঝে মাঝে নিজেরই বিরুদ্ধে নিজের ব্যবহার করা এসব মারণাস্ত্র ছাড়া মানব কখনোই পৃথিবীর অধীশ্বর হতে পারত না। এ কাজেই সে নিজের সবটুকু দক্ষতা ঢেলে দিয়েছে। যুগ যুগ ধরে সেগুলো কাজও দিয়েছে বেশ।
কিন্তু আজ সহসাই সে সেসব রক্ষাকারীর কারণেই জীবন চালাচ্ছে ধার করা সময়ের উপর ভর করে।
২. টি এম এ-১
দ্বিতীয় পর্ব : টি এম এ-১
অধ্যায় ৭. স্পেশাল ফ্লাইট
যতবারই পৃথিবী ছেড়ে যাই না কেন, ডক্টর হেউড ফ্লয়েড আপনমনে বিড়বিড় করছে, যাবার উত্তেজনা সব সময়ই নতুন। তার মঙ্গলে যাওয়া হল একবার, চাঁদে তিনবার আর বাইরের স্পেস স্টেশনগুলোতে যে কতবার তার ইয়ত্তা নেই। অথচ আজো টেক অফের মুহূর্তটা এগিয়ে এলেই একটা বাড়ন্ত টেনশন টের পায়। বিস্ময় আর ভয়ের এক অনুভব-এবং, হ্যাঁ, সাথে একটু নার্ভাসনেস–সাথে সাথে সেই পুরনো পাগলামি, ঘরকুনো কুয়োর ব্যাঙের মতো পৃথিবীর প্রতি টান। যে কোনো কূপমণ্ডুক পৃথিবীপ্রেমী প্রথমবার গ্রহ ছেড়ে যাবার সময় যেমন অনুভব করে, ঠিক তেমনি।
মাঝরাতে প্রেসিডেন্টের সাথে ব্রিফিং ছিল। ব্রিফিংয়ের পর যে জেটটা তাকে ওয়াশিংটন থেকে উড়িয়ে এনেছে সেটা হারিয়ে যাচ্ছে অতি পরিচিত এক পরিবেশের ওপাশে। আজো তার কাছে চারপাশের দৃশ্যটা অপার্থিব মনে হয়। এখানেই স্পেস এজ বা নাক্ষত্রিক কালের প্রথম দু প্রজন্মের উত্থান; ফ্লোরিডার সাগর তীরের বিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। দক্ষিণটা মিশে গেছে মিটমিটে লাল ওয়ার্নিং লাইটের আলোয়; শেষ মাথা উদ্ভাসিত হয়ে আছে স্যাটার্ন আর নেপচুনের পথের গ্যানট্রিতে। দূরতম প্রান্তে দেখা যায় আলোর বন্যায় ভেসে যাওয়া রূপালী বিশাল জাতীয় মিনারটা। এটা সর্বশেষ স্যাটার্ন ভি’ স্মৃতিস্তম্ভ। পাদদেশে নিয়মিত সম্মেলন আর মেলা বসে।
কাছাকাছিই, আকাশের বিপরীতে দেদীপ্যমান এক বিশাল ভবন। ঠিক যেন মানুষের গড়া পর্বত। ‘দ্য ভেহিকল অ্যাসেম্নি বিল্ডিং’ আজো পৃথিবীর বুকে সবচে বড় কীর্তি।
কিন্তু এসবই অতীতের সম্পদ, আর তার যাত্রা ভবিষ্যতের পথে। বালুকাবেলার দিকে যেতে যেতে ডক্টর ফ্লয়েড তার নিচে বিল্ডিংয়ের গোলকধাঁধা দেখতে পায়, এরপরই এক বিশাল এয়ারস্ট্রিপ; তার পর এক চওড়া, মরার মতো সোজা দাগ চোখে পড়ে। এটাই সেই দানবীয় লঞ্চিং ট্র্যাক, নিচের দাগগুলো সেই ট্র্যাকের রেলপথ। শেষমাথা যানবাহন আর গ্যানট্রিতে বোঝাই; আরেক কোণায় উজ্জ্বল আলোর ভুবনে বসে আছে এক ঝকঝকে স্পেসপ্লেন। যে কোনো সময় উড়াল দিতে পারবে তারার দেশে। আচমকা সে ভুলে বসেছে নিজের উচ্চতাকে, হঠাৎই তার মনে হয় নিচে বুঝি এক সুন্দর রূপালী শুয়োপোকা বসে আছে কোনো টর্চের আলোর সামনে।
এরপর ছোট ফ্লুয়িং যন্ত্রপাতিগুলোর আকার তার সামনে সেই ‘মথ’ এর প্রকৃত গড়ন ধরিয়ে দেয়। এটার ডানার সবচে চিকন ভি আকৃতির জায়গাতেও বিস্তার হবে কমপক্ষে দু’শ ফিট। আর ঐ অসম্ভব বড় যানটা-ডক্টর ফ্লয়েড অবিশ্বাসী আর গর্বিত মনে নিজেকে শোনায়-অপেক্ষা করছে শুধু আমার জন্য। যতটুকু তার মনে পড়ে, মাত্র একজনকে চাঁদে বয়ে নেয়ার জন্য এর আগে কোনো মিশন সেট করা হয়নি।
যদিও এখন ভোর দুটো, একদল সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যান তাকে ঘেঁকে ধরে ওরিয়ন থ্রি স্পেসক্র্যাফটের ফ্ল্যাডলাইটের আলোয়। সে ন্যাশনাল কাউন্সিল অন অ্যাস্ট্রোনটিক্সের চেয়ারম্যান হিসেবে তাদের অনেককেই আগে থেকে চিনত। আমেরিকার জাতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান কাউন্সিলের সভাপতি হওয়াটাতো চাট্টিখানি কথা নয়। হাজার হলেও, সাংবাদিক সম্মেলন তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু এখানে এমন কিছু আয়োজনের সময় সুযোগ বা স্থান-কোনোটাই নেই। সবচে বড় কথা, তার বলার কিস্যু নেই; তাতে কী, কম্যুনিকেশন মিডিয়ার লোকজনকে আঘাত দিয়ে কথা না বলাই সুবোধ বালকের কাজ।
‘ডক্টর ফ্লয়েড? আমি অ্যাসোসিয়েটেড নিউজের জিম ফ্রস্টার। আপনি কি এ ফ্লাইট নিয়ে দু-চার কথা বলতে পারবেন আমাদের সাথে?’
‘আই অ্যাম ভেরি স্যরি-একটা কথাও বলতে পারব না।’
‘কিন্তু আপনি ঠিকই আজ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছেন। এবার এক পরিচিত স্বর কথা বলে ওঠে।
‘ওহ-হ্যালো, মাইক। তুমি বেচারা শুধু শুধু আরামের বিছানা ছেড়ে এসেছ। অবশ্যই, কোনো মন্তব্য করা যাচ্ছে না।’
‘আপনি অন্তত এটা বলুন, চাঁদে কি কোনো রোগ ছড়িয়ে পড়ছে?’ এক টিভি রিপোর্টার আশ্চর্য দক্ষতায় তার পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে তাকে ঠিকই নিজের ছোট্ট টিভি ক্যামেরার ফ্রেমে ধরে রাখতে রাখতে বলে চলেছে।
‘স্যরি।’ মাথা নাড়তে নাড়তে ডক্টর ফ্লয়েড বলে।
‘রোগ নির্মূলের ব্যাপারে কী করছেন আপনারা?’ আরেক রিপোর্টার আবার বা হাত ঢোকায়, ‘কদ্দিন লাগবে সেরে উঠতে?’
‘এখনো, কোনো কথা নয়।
‘ডক্টর ফ্লয়েড!’ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক অতি খাটো আর পরিশ্রমী মহিলা প্রেসকর্মী, চাঁদের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধের কী ব্যাখ্যা করবেন আপনারা? এর সাথে রাজনীতির ঘোঁট পাকানোর কোনো সম্বন্ধ নেইতো?’।
‘রাজনীতির কোন ঘোঁট পাকানো?’ কাঠখোট্টা বে রহম সুরে ডক্টর ফ্লয়েড প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। হাসির ছোটখাট ফোয়ারা ছুটে যায় চারদিকে। হাল না ছাড়া সাংবাদিকের দল এবার বিদায় দেয় অপ্রসন্নচিত্তে, হ্যাভ এ গুড ট্রিপ, ডক্টর।
সাংবাদিকরা যে এমনি এম্নি ছেড়ে দিয়েছে তা নয়। ফ্লয়েড আগেই ঢুকতে শুরু করেছিল গ্যানট্রির নিরাপত্তা বেষ্টনীতে।
যদ্দুর তার মনে হয়, এটা কোনো বড়সড় স্থায়ী সংকট নয়। উনিশশো সত্তরের পর থেকে পৃথিবীকে দু সমস্যা নিয়ে বিভক্ত করা হয় আর তার একটা দিয়ে অন্যটাকে কাটিয়ে দেয়া যায়।
যদিও জন্মনিয়ন্ত্রণ সহজ, স্বল্প ব্যয়ের প্রক্রিয়া, এবং সব ধর্ম অনুমোদিত-তবু অনেক দেরি হয়ে গেছে; আজ পৃথিবীর জনসংখ্যা ছ বিলিয়ন; ছ’শ কোটি। আর তার এক তৃতীয়াংশ চৈনিক সাম্রাজ্যে। দু-সন্তান নিয়ে আইন, সুযোগ-সুবিধা আর প্রচারণা করা হয়েছে বেশ। কিন্তু সেসবের প্রয়োগ হয়নি ঠিকমতো। ফলে প্রতি দেশেই খাদ্যের চরম সংকট। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও মাংসহীন দিবস রয়েছে। পনের বছরের সংকটময় মঙ্গা মানুষকে সাগরের দ্বারস্থ করে, সিন্থেটিক ফুডের খোঁজে লেগে যায় সবাই।
এর আগে কখনোই আন্তর্জাতিক সহায়তা আর সুসম্পর্ক এত জরুরী ছিল না। অথচ আজকের মতো এত বেশি হবু রণাঙ্গনও ছিল না আগে কখনো। লাখো বছরে মানবজাতি তার হিংস্রতার খুব একটা খোয়াতে পারেনি। সিম্বলিক চিত্রগুলি শুধু রাজনীতিবিদদের চোখেই ধরা পড়ে; আটত্রিশ পারমাণবিক শক্তিধর দেশ একে অন্যের উপর অহর্নিশি শ্যেন দৃষ্টি রেখে চলেছে। তাদেরকে আবার অনেক অনেক মেগাটন পারমাণবিক বর্জ্য সরিয়ে দিতে হবে পৃথিবীর আহত বুক থেকে। অথচ, অবাক লাগলেও সত্যি কথা, কখনো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। অবশ্য এই অবস্থা যে কদ্দিন চলবে তা কেউ জানে না।
আর আজকাল চীন তাদের প্রয়োজনের খাতিরে নতুন ছোট দেশ এবং গোষ্ঠীর একেবারে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে পঞ্চাশ ওয়্যারহেডসম্পন্ন একটা পরিপূর্ণ পারমাণবিক যুদ্ধক্ষমতা। খরচ পড়বে বিশ কোটি মার্কিন ডলারেরও কম। এ বিকিকিনি নিয়ে সরকারের সাথে যে কোনো সময় যোগাযোগ করা যায়। সেই ঢিমেতাল সরকারি লাল ফিতার দৌরাত্ম এই একটা ক্ষেত্রে নেই।
চৈনিকরা নিজেদের ভয়ানক অস্ত্রের ভান্ডারকে হার্ড মানিতে পরিণত করে ডুবন্ত অর্থনীতিকে টেনে তুলতে চাইছে-এ মতো কেউ কেউ দেন। অথবা তারা এমন ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করেছে যার সামনে এসব খেলনার আর কোনো দাম নেই। লোকজন বলে বেড়ায় যে রেডিও হিপনোসিস বা দূর থেকে সম্মোহিত করার পদ্ধতি বের করেছে অনেকেই। দূর-সম্মোহন করা যায় সামান্য স্যাটেলাইট ব্যবহার করে। অনেকে বলে শক্তিময় ভাইরাসের কথা। এমন সব কৃত্রিম রোগের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করার জোর গুজব রটেছে বাজারে যেগুলোর ওষুধ শুধু রোগের স্রষ্টার কাছেই পাওয়া যাবে। মজার আইডিয়াগুলো হয় স্রেফ অপপ্রচার, নয়তো অলীক কল্পনা। কিন্তু এসব ধারণার কোনোটাকেই মাথা থেকে তাড়িয়ে দেবার তিলমাত্র জো নেই। প্রতিবার ফ্লয়েড পৃথিবী ছাড়ার সময় আরেক ভয় পায় ফিরে এসে গ্রহটার দেখা পাবো তো? কে জানে!
কেবিনে ঢোকার সাথে সাথে বিমানবালা তাকে স্বাগত জানাল। মুখে মাপা হাসি, ‘গুডমর্নিং, ডক্টর ফ্লয়েড, আমি মিস সিমন্স- আপনাকে এখানে আমাদের ক্যাপ্টেন টিন্স আর কো পাইলট, ফাস্ট অফিসার ব্যালার্ডের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি।’
‘থ্যাঙ্ক ইউ’ বলতে বলতেই ডক্টর ফ্লয়েড ভাবে, কেন যে স্টুয়ার্ডেসগুলো সারা জীবন রোবট স্পেস গাইডের মতো কথা বলে আল্লা মালুম।
‘পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টেক অফ হবে,’ বিশজন যাত্রীর খালি কেবিনটার দিকে হাত নাড়তে নাড়তে মেয়েটা বলছে, যে কোনো সিটে বসতে পারেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন টিন্স মনে করেন আপনি ডকিং অপারেশন দেখতে চাইলে প্রথম জানালার বামপাশের আসনটায় বসলে ভাল হয়।
‘তাই করব আমি।’
মাথার উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে মহাকাশবালা বেরিয়ে যায়। কারণ তার কিউবিকলটা পেছনদিকে।
জায়গামতো বসে ফ্লয়েড সেফটি হার্নেস জড়িয়ে নেয়; বেঁধে নেয় কাঁধ। তারপর ব্রিফকেসটা রাখে সামনে। মুহূর্তখানেক পরেই লাউডস্পিকার মৃদু বাড়তি শব্দ করে সরব হয়ে উঠল, ‘শুভ সকাল,’ বলছে মিস সিমন্সের গলা, ‘এটা স্পেশাল ফ্লাইট থ্রি, কেনেডি থেকে স্পেস স্টেশন ওয়ানের দিকে যাত্রা করব আমরা।’
ব্যাপারস্যাপার দেখে মনে হয় এই মেয়ে পুরো পোশাকী রীতি মেনে চলতে একেবারে যাকে বলে বদ্ধপরিকর। এবার আর ডক্টর ফ্লয়েড হাসি ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, কারণ ঠিক সেভাবেই হোস্টেসের কথা এগিয়ে যাচ্ছে।
‘আমাদের ট্রান্সমিট টাইম হবে পঞ্চান্ন মিনিট। সর্বোচ্চ ত্বরণ হবে টু জি২, আর ওজনশূন্য থাকব ত্রিশ মিনিটের জন্য। নিরাপত্তা বাতি জ্বলার আগ পর্যন্ত সিট ছাড়বেন না, প্লিজ।
ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো ফ্লয়েড, বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ।’
জবাবে তার পাওনা হয় একটা হালকা, মিষ্টি, সুন্দর, মনোহর কিন্তু চরম পেশাদার হাসি।
নিজের আসনে হেলান দিয়ে এবার সে একটু আরাম করে নেয়। এ ট্রিপের জন্য করদাতাদের ঘাড়ে এক মিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি বোঝা চাপবে। কিন্তু সে জানে, তার কাজে সে ঠিকই পারঙ্গম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনে ফিরে গেলেই কি বেশ হয় না? একটা গ্রহ-জগৎ তথা প্ল্যানেটারি সিস্টেমের গঠন নিয়ে করতে থাকা গবেষণার বাড়তি কাজটা আর শেষ হলো না। কিন্তু আজ আর বয়েস নেই। কাজটাতো অন্যভাবেও করা যায়।
‘স্বয়ংক্রিয় কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যাচ্ছে এখন,’ ক্যাপ্টেনের স্বর ভেসে আসে স্পিকারের ভিতর দিয়ে। টি চ্যাটের মাধ্যমে হালকা কোমল গানও ভেসে আসছে।
‘উপরে উঠছি এক মিনিটের মধ্যেই।’
আর সব সময়ের মতো আজো এ মুহূর্তটুকুকে একটা ঘণ্টার মতো লম্বা মনে হয়। তার চারপাশ পেচিয়ে যে দানবীয় শক্তি কাজ করছে সে সম্পর্কে মুহূর্তেই সচেতন হয়ে ওঠে সে। এ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকে। দুটো স্পেসক্রাফটের জ্বালানী ট্যাঙ্ক আর লঞ্চিং ট্র্যাকের শক্তি সংগ্রহ সিস্টেমে প্রায় একটা পারমাণবিক বোমার সমান শক্তির যোগান দেয়া হয়েছে। এর সবটুকু ব্যয় হয় শুধু তাকে পৃথিবী থেকে মাত্র দু’শ মাইল উপরে উঠিয়ে নিতে।
আজকাল কাউন্ট ডাউনে আর মান্ধাতা আমলের ফাইভ-ফোর-থ্রি-টু-ওয়ান জিরোর কারবার নেই। সেগুলো মানুষের স্নায়ুতে বেশ ভালো চাপ ফেলে।
‘পনের সেকেন্ডের মধ্যে উড্ডয়ন। ভালো লাগবে যদি গভীর করে শ্বাসপ্রশ্বাস নেন।’
এটা দারুণ মনস্তত্ত্ব আর শরীরতত্ত্বের সংমিশ্রণ। ফ্লয়েড নিজেকে অক্সিজেনে যথাসম্ভব টইটম্বুর করে নেয়। প্রস্তুত করে নেয় যে কোনো কিছুর জন্য। এই বিশাল যানটা তার হাজার টনী শরীর নিয়ে আটলান্টিকের উপর উড়ছে বর্তমানে।
কখন তারা ট্রাক ছেড়ে আকাশের সন্তান হয়েছে তা কেউ ঠিক ঠিক বলতে পারবে না কিন্তু রকেটের তর্জনগর্জন দ্বিগুণ হয়ে যাবার সাথে সাথে সিট কুশনের আরো আরো গভীরে ডুবে যায় ফ্লয়েড। ফার্স্ট স্টেজ ইঞ্জিন ছেড়ে দেয়া হয়েছে। খুব ইচ্ছা হয় একবার বাইরে চেয়ে জিনিসটার পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া দেখতে, কিন্তু নিজের ঘাড়টা ফেরানোও এখন নিতান্তই কষ্টকল্পনা। অবাক হলেও সত্যি, এখনো আরামের একবিন্দু কমতি নেই। বরং গতিবৃদ্ধির দুর্দান্ত চাপ আর মোটরগুলোর দারুণ গর্জন এক আধিভৌতিক চরম শিহরন এনে দেয়। কান ঝাঁঝ করছে, রক্তপ্রবাহ শিরা উপশিরায় দেবে দেবে যাচ্ছে, এবার আবারো ফ্লয়েড বাকী জীবন থেকে বেশি ‘জীবন্ত’ হয়ে উঠছে। আবার ফিরে এসেছে দুর্দান্ত তারুণ্য, আবার তার গলা ফাটিয়ে গাইতে ইচ্ছা করছে। গাওয়ার কাজটা এক্কেবারে নিরাপদ, কোনো ব্যাটার শোনার ক্ষমতা নেই ইঞ্জিনের এই গগনবিদারী তারস্বরের সামনে।
স্ফূর্তির ভাবটা কেটে গেল জলদি জলদিই। মনে পড়ে গেছে যে সে পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছে, ছেড়ে যাচ্ছে সারা জীবনের সবটুকু ভালবাসা। নিচে তার তিন সন্তানের বাস, তিন এতিম সন্তান! দশ বছর আগে তাদের মা ইউরোপের সেই মরণ প্লেনে ওঠার পর…(দশ বছর? অসম্ভব! এখনো মনে হয় যেন…) তাদের জন্য হলেও তার বিয়ে করা উচিত ছিল আবার…
যখন চাপ আর শব্দ আস্তে আস্তে কমে আসে আর কেবিনের লাউড স্পিকার চেঁচিয়ে ওঠে, এবার লোয়ার স্টেজ ছেড়ে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, শুরু হল…’ তখনো সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কতটা সময় পেরিয়েছে এতক্ষণে।
একটা ছোট ঝুঁকির সাথে সাথে আবার মনে পড়ে যায় লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সেই প্রদর্শনীর কথা। সেটা দেখেছিল নাসা অফিসে:
মহাপাখির পিঠে আরেক মহাপাখির উড্ডয়ন হবে, যে কুটিরে এর জন্ম সেটা গর্বে হবে উজ্জ্বলতর।
আচ্ছা, আজ সেই দ্য গ্রেট বার্ড উড়ছে, দ্য ভিঞ্চির সবটুকু স্বপ্নকে পুঁজি করে উড়ছে। এর ছেড়ে দেয়া সাথী ফিরে চলেছে পৃথিবীতে। দশ হাজার কিলোমিটারের ধনুক তৈরি করে খালি পোয়ার স্টেজটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাবে। এর কাজ বাড়তি গতি দেয়া। মূল যানকে একটু উঠিয়ে দিয়ে পরের বার একই কাজ করার জন্য ফিরে যাবে নিজের বাড়িতে, কেনেডিতে। কয়েক ঘণ্টায় জ্বালানী ভরে নিয়ে, ঘষামাজা শেষ হলে আবার নতুন কোনো সঙ্গীকে উপরের জ্বলজ্বলে নিরবতায় উঠিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে। সব সঙ্গীকে সেই উচ্চতায় পৌঁছে দেবে যেখানে সে নিজে যেতে পারবে না কোনোদিন।
এতক্ষণে-ভাবছে ফ্লয়েড-আমরা অর্বিটের বেশিরভাগ পৰ্থ পেরিয়ে এসেছি। আপার স্টেজের রকেট জ্বলে উঠল; আবার ফিরে এল ত্বরণ। এবারের গ্র্যাভিটিটা অনেক বেশি ভদ্রগোছের। আসল কথা, স্বাভাবিক মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে এক বিন্দু বেশি অনুভূত হয় না। কিন্তু হাঁটার চিন্তা নিতান্তই অবান্তর, কারণ আকর্ষণ ফিরে এসেছে ঠিকই, উল্টো দিকে। তার মাথার পিছন দিকটাই এখন নিচ। সে যদি সিটবেল্ট ছেড়ে দেয়ার মতো বোকা হয়, তাহলে সোজা গিয়ে পড়বে কেবিনের পেছনে, দেয়ালে।
এই কিম্ভুত মনোভাব কেটে যাবে যদি ভাবা যায় যে শিপ দাঁড়িয়ে আছে লেজের উপর, আরাম করে। ফ্লয়েড দেখে বাকী সব সিট তার কাছে নিচের দিকের মই বা সিঁড়ির ধাপের মতো লাগছে, কারণ সে সবচে সামনের আসনে বসা। সূর্যালোকে তরীর বাইরের দিকটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ডক্টর ফ্লয়েড এই সম্মোহন কাটানোর চেষ্টা করে প্রাণপণে।
কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারা লালচে বেগুনী, গোলাপী, সোনালী আর নীল পর্দার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে চোখ ধাঁধানো সাদায়। জানালাগুলো আলোর তীব্রতা প্রতিরোধের জন্য ভালমতো রঙচঙা করা হয়েছে। তার পরও সূর্যের অত্যুৎসাহী সর্বগ্রাসী আলো ফ্লয়েডের চোখে সামান্য সময়ের জন্য একটা রশ্মি বুলিয়ে দিয়ে বেচারাকে কয়েক মিনিটের জন্য একদম অন্ধ করে দিয়ে গেল। সে আসলেই মহাকাশ ভ্রমণ করছে, কিন্তু হায়, নক্ষত্র দেখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।
চোখগুলোকে হাতে ঢেকে নিয়ে সে বাইরে উঁকি দেয়ার চেষ্টা চালায় একটু। সেখানে দিনের আলোয় বাড়তি ডানাটা তপ্ত ধাতুর মতো চকচক করছে। চারপাশে অসীম আঁধার, সে অন্ধকারটা নিশ্চয়ই তারায় তারায় ভরা! দেখাই যায় না সেগুলোকে।
ধীরেসুস্থে ফিরে আসছে ওজন। শিপ নিজেকে অর্বিটে বসিয়ে নেয়ার সাথে সাথে নিভে গেছে রকেটের জ্বালামুখ। ইঞ্জিনের বজ্রপাতগুলো মিইয়ে আসে, তারপর চাপা একটু হিসহিসানি, সবশেষে পথ খুঁজে নেয় নিরবতার ভিতরে। পুনঃশক্তি সংগ্রহ স্ট্রাপ না থাকলে ফ্লয়েড ঠিকই সিট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত; কারণ তার পাকস্থলি বিপদসংকেত জানান দিচ্ছে। তার প্রাণান্ত ভাবনা, আধঘণ্টা আগে দশ হাজার কিলোমিটার দূরে যে পিলগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো আশানুরূপ কাজ দেবে। অবশ্য জীবনে মাত্র একবারই স্পেসসিক হয়েছিল। সী সিকনেস, স্পেস সিকনেস…যত্তসব! এ অবস্থাটা সহজে আসেও না।
কেবিনের স্পিকারে ভেসে আসা পাইলটের স্বর স্থির আর অবিচল, অনুগ্রহ করে জিরো জি’র সব নিয়মকানুন দেখে নিন। আমরা স্পেস স্টেশন ওয়ান এর সাথে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে মিলিত হব।’
স্টুয়ার্ডেস সিটগুলোর মাঝের সরু জায়গা পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। তার পদক্ষেপে কিছুটা অস্বাভাবিকতা। যেন পা প্রতিবার মেঝেতে পড়ে যাবার পরই আঠায় আটকে যাচ্ছে। সে পা রাখছে ফ্লোরে বিছানো ভেলক্রো কার্পেটে। এ কার্পেট আছে ছাদের গায়েও। কার্পেট আর তার স্যান্ডেলের সুখতলি অতি সূক্ষ্ম হুক দিয়ে ঢাকা। হুকগুলো একে অপরকে জড়িয়ে ধরতে পারে ঠিকমতো। চলাচলের এই কৌশল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা অনভ্যস্ত যাত্রীদের এক কাতারে দাঁড় করায়, বাঁচায় অস্বস্তির হাত থেকে।
‘আপনি কি একটু চা বা কফি পান করবেন, ডক্টর ফ্লয়েড?
‘না। ধন্যবাদ তোমাকে।’ একটু হেসে জবাব দেয় সে। ঐসব টিউবওয়ালা জিনিসে করে কিছু খেলে নিজেকে সব সময় একেবারে বাচ্চা বাচ্চা মনে হয়।
যখন সে ব্রিফকেস খুলে কাগজপত্র ঢোকাচ্ছে তখনো মেয়েটা আগের মতোই ঘুরঘুর করছে আশপাশে।
‘ডক্টর ফ্লয়েড, একটা প্রশ্ন করতে পারি আপনাকে?’
‘অবশ্যই।’ চশমা পরে তাকাতে তাকাতে উত্তর দেয় সে।
‘আমার… হবু বর ক্ল্যাভিয়াসের একজন ভূতত্ত্ববিদ।’ স্পষ্ট করে নিজের প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করছে সে, ‘এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ওর সাথে কথা হয় না।’
‘দুঃখ পেলাম শুনে। হয়তো সে কাজের জন্য বাইরে গেছে। চাঁদে দিন সাতেক বেসের বাইরে থাকা বিচিত্র কিছু নয়।’
সাথে সাথেই মাথা নাড়ে মেয়েটা, এমন হয়, কিন্তু আগে আগেই ও আমাকে বলে রাখে। সব সময়। বুঝতেই পারছেন এ পরিস্থিতিতে আমি কীরকম ভেঙে পড়েছি চারপাশের গুজব শুনে। আসলেই কি চাঁদে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে?
‘এমন হয়ে থাকলে যোগাযোগ বন্ধ হবে কোনো দুঃখে? আর হলে সতর্ক হওয়ারও কিছু নেই। দারুণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সেখানে। আটানব্বইয়ের কথা মনে আছেতো? ফ্লু ভাইরাস বিবর্তিত হয়ে অ্যাটাক করেছিল। অনেক লোক অসুস্থ হলেও কেউ মারা যায়নি। আসলে এটুকুই আমি বলতে পারি। এরচে বেশি এক কণাও না। ভদ্রভাবে শেষ করে সে কথাটা।
মিষ্টি করে হেসেই সুদর্শনা মিস সিমন্স সোজা উপরদিকে চলে যায়।
‘আচ্ছা, ধন্যবাদ, ডক্টর, আপনাকে বিরক্ত করায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’
‘একটুও বিরক্ত করোনি।’ সে উষ্ণভাবে বললেও কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। এরপরই নিজেকে ডুবিয়ে দেয় টেকনিক্যাল রিপোর্টের অথৈ সাগরে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যয় করে পেছনের দিনগুলোর কাজের তালিকায় মগ্ন হয়ে।
একবার চাঁদে পৌঁছে গেলে আর পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে না।
অধ্যায় ৮. কক্ষপথে দেখা
আধঘণ্টা পরে পাইলট ঘোষণা করল, ‘আর দশমিনিটের মধ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করছি। প্লিজ সিট হার্নেসটা দেখে নিন।’
বাধ্য ছেলের মতো ফ্লয়েড কথাটা পালন করে নিজের কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে। শেষদিকের অর্বিটের ঝাঁকিতে পড়াশোনা করা খুব একটা ভালো না–এমন কথা বলা হয়। এ অবস্থা চলছে গত তিনশো মাইল জুড়ে আসার সময়। এ সময়টায় বরং চোখ বন্ধ করে রাখাই শ্রেয়। কারণ রকেটের হঠাৎ প্রজ্বলন বেশ ঝাঁকাঝাঁকি শুরু করে।
কয়েক মিনিট পরেই সে চোখের সামনে কয়েক মাইল দূরে আবছায়ার মতো হালকাভাবে স্পেস স্টেশন ওয়ানকে দেখতে পেল। মানুষ কোথায় চলে গেছে! সে চাঁদ থেকে পৃথিবীতে যায়, পৃথিবী থেকে যায় চাঁদে; মধ্যিখানে শূন্যের স্টেশনেও একটু জিরিয়ে নেয়। স্টেশনের পালিশ করা ধাতব গায়ে সূর্যালোক যেন পিছলে যাচ্ছে সারাক্ষণ। প্রায় দু’শ আশি মিটার ব্যাসের চাকতিটা খুব বেশি দূরে নয়। একটা টিটভ ফাইভ শ্রেণীর স্পেসপ্লেন ধীরে ভেসে বেরিয়ে আসছে একই অর্বিট ধরে। দেখতে প্রায় একটা এ্যারেস ওয়ান বি ওয়ার্ক হর্সের মতোই। এর পা-গুলোও চাঁদে অবতরণের উপযোগী করে তৈরি করা। চার পা-ই শক অ্যাবজর্ভিং।
ওরিয়ন থ্রি স্পেসক্র্যাফট একটা উচ্চ শক্তির অর্কিট থেকে বেরিয়ে আসছিল বলে পৃথিবীকে স্টেশনের পেছনে অবাক করা রূপে দেখা যায়। দু’শ মাইল উচ্চতা থেকে ফ্লয়েড স্পষ্ট দেখতে পায় আফ্রিকার বেশিরভাগ অঞ্চল আর সুবিশাল অতলান্তিককে। যথেষ্ট মেঘ আছে। তবু গোল্ড কোস্টের[১৪] সবুজ সীমারেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।
ডকিং আর্ম সহ স্পেস স্টেশনের কেন্দ্রীয় অক্ষ বেরিয়ে আসছে। যেন সতরে আসছে মহাকাশের মহানদী বেয়ে। কেন্দ্রীয় অক্ষের ধারক অংশ, অক্ষ, ডকিং আর্ম একেবারেই ঘুরছে না। আরেকভাবে বলতে গেলে উল্টো হয়ে যায়, এগুলো ঘুরছে এবং বেশ ভালোভাবেই ঘুরছে। স্পেস স্টেশনের বাকী অংশের বিপরীত গতিতে ঘোরায় স্থির মনে হয়। এ অক্ষ স্থির না থাকলে আসতে থাকা কোনো স্পেসক্রাফট এর সাথে যুক্ত হতে পারবে না। তাই সেই আগুয়ান খানের সাপেক্ষে স্থির থাকতে হচ্ছে। মানুষ আর জিনিসপাতির দঙ্গলকে নামানোর ক্ষেত্রে দারুণ অসুবিধা হতো যদি স্পেস স্টেশনের মতো এটাও ঘুরে চলত ভয়ংকরভাবে।
একেবারে হাল্কা আওয়াজ তুলে, ক্ষীণ ধাক্কা দিয়ে স্টেশনের সাথে মহাকাশযান মিলিত হল। বাইরে থেকে ধাতব ঘষটানোর শব্দ আসে। বাতাস আর বায়ুচাপের সমন্বয় আর সমতার জন্য হালকা হিসহিস শব্দও ওঠে। কয়েক সেকেন্ড পরেই স্পেস স্টেশনের হালকা ইউনিফর্ম পরা এক লোক ভিতরে এল।
‘আপনার দেখা পেয়ে খুশি হলাম, ডক্টর ফ্লয়েড। আমি নিক মিলার, স্টেশন সিকিউরিটি; শাটল ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত আপনার দেখভালের দায়িত্বটা আমার কাঁধেই পড়েছে।’
তারা হ্যান্ডশেক করার পর ফ্লয়েড বিমানবালার দিকে তাকিয়ে একটু হাসি দেয়, ‘প্লিজ, আমার পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন টিন্স আর কো পাইলটকে ধন্যবাদ দিও। আশা করি যাবার পথে তোমাদের সাথে দেখা হবে।’
খুব সতর্কভাবে সে নড়াচড়া করছে, কারণ প্রায় বছরখানেক হতে চলল সে ওজনশূন্যতায় পড়েনি। ওজনহীনতায় চলাফেরার অভ্যাসটা ফিরে আসতে একটু সময় নেবে; লোকে অভ্যাসটাকে বলে স্পেসলেগ অর্থাৎ কিনা মহাকাশের অদৃশ্য পা। নিজেকে ঠিক রাখতে এয়ারলকের ভিতর দিয়ে স্পেস স্টেশনের গোলাকার ঘরটায় যেতে যেতে সে হাত ঠেকায় উপরের দেয়ালে। এই ঘরে ভালোমতো প্যাড লাগানো হয়েছে, তার উপর চারদিকে গিজগিজ করছে হ্যান্ডহোন্ড। পুরো চেম্বারটা ঘুরতে শুরু করেছে। এবার ফ্লয়েড একটা হ্যান্ডহোল্ড ধরে বসে ঠিকমতো। এই ঘুর্ণণ এক সময় স্পেস স্টেশনের ঘোরার দিকে একইভাবে চলতে থাকবে।
গতি বাড়তে শুরু করলেই অভিকর্ষের ভৌতিক আঙুল এসে তাকে খোঁচাতে থাকে আর সে ধীরে ভেসে যায় দেয়ালের দিকে। এবার সে এর উপরে সামনে পেছনে দৌড়ে দাঁড়িয়ে থাকছে যেভাবে কোনো সমুদ্রের বিশেষ স্রোত প্রবাহে প্রবাল গড়িয়ে চলে। নিচের মেঝেটাকে কুঁকড়ে যেতে দেখা কী ভয়াবহ ব্যাপার! অবশেষে স্টেশনের কেন্দ্রমুখী বল তার দখল নিয়ে নিল। কেন্দ্রের দিকে বলটা বেশ দুর্বল হলেও পরিধির দিকে যেতে থাকলে ক্রমান্বয়ে বাড়বে।
সেন্ট্রাল ট্রানজিট চেম্বার থেকে ফ্লয়েড মিলারকে অনুসরণ করে একটা বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। প্রথমদিকে বল এত কম ছিল যে নিচে নামতে হলে জোর দিয়ে নামতে হয়েছে। সে এই বিশাল ঘুরন্ত চাকতির একেবারে বাইরের দিকে চলে এল। এবার একটু একটু স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করা যাচ্ছে।
গত এক বছরে লাউঞ্জটাকে নানা সুবিধা দিয়ে নতুন করে সাজানো হয়েছে। আগের ছোট চেয়ার, নিচু টেবিল, রেস্তরা আর পোস্ট অফিস ছাড়াও এবার এতে একটা করে চুল কাটার দোকান, স্যুভেনির শপ, ওষুধের দোকান আর আস্ত থিয়েটার বসানো হয়েছে। স্যুভেনির শপটায় পৃথিবী আর চাঁদের চমৎকার সব প্রাকৃতিক দৃশ্য, গ্যারান্টি দেয়া চাঁদের পাথর, সব বড় অভিযাত্রী আর বড় বড় মানুষের মূর্তি পাওয়া যায় প্লাস্টিকে, শুধু দামটাই অবিশ্বাস্য চড়া।
‘অপেক্ষা করার সময় কিছু খাবেন? হাতে আরো ত্রিশ মিনিট সময় আছে।’
‘দু-টুকরো চিনির সাথে এককাপ ব্ল্যাক কফি। আর কল করতে চাই পৃথিবীতে।’
‘ঠিক আছে, ডক্টর। আমি কফি আনছি, ফোনগুলো ঐদিকে।’
ফোনবুথের সামনে দুটো বাঁধা, একটায় লেখা ‘সোভিয়েত সেকশনে স্বাগতম’ আর অন্যটায় আছে, ‘ইউ এস সেকশনে’ স্বাগতম। নিচেই স্প্যানিশ, রাশিয়ান, ইংলিশ, চাইনিজ, ফ্রেঞ্চ আর জার্মান ভাষায় লেখা:
দয়া করে প্রস্তুত করুন আপনার:
পাসপোর্ট
ভিসা
মেডিক্যাল সার্টিফিকেট
যাতায়াতের অনুমতিপত্র
ওজনের ঘোষণা
এক্ষেত্রে ব্যাপারটা সুবিধাজনক বলতে হয়। কারণ একাধিক বুথ থাকছে। এই বুধগুলো থেকে বেরুতে পারলেই যাত্রীরা মিলেমিশে আবার এক হয়ে যায়। তখন কোনো সোভিয়েত–মার্কিন ঘেঁষাঘেঁষি নেই। এ বিভক্তি শুধুই প্রশাসনিক।
ফ্লয়েড আবারো দেখে নেয়। না, ইউ এস এরিয়া কোড আজো একাশিই রয়ে গেছে। তারপর নিজের বাসার বারো সংখ্যার নম্বরটায় ডায়াল করে। সকল কাজের কাজি প্লাস্টিক ক্রেডিট কার্ডটা পরিশোধ স্লটে প্রবেশ করিয়ে আধ মিনিট অপেক্ষা করেই বাসায় লাইন পেয়ে গেল।
ওয়াশিংটন এখনো ঘুমের রাজ্য, কারণ ভোর হতে কয়েক ঘণ্টা বাকী, কিন্তু সে কাউকে বিরক্ত করবে না। জেগে ওঠার সাথে সাথেই হাউসকিপার কল পেয়ে যাবে।
‘মিস ফ্লেমিং- ফ্লয়েড বলছি। স্যরি, তাড়াহুড়ো করে পৃথিবী ছাড়তে হল। আমার অফিসে কল করে গাড়িটা ডালাস এয়ারপোর্ট থেকে যোগাড় করে নিতে বলবে। চাবিটা সিনিয়র ফ্লাইট কন্ট্রোল অফিসার মিস্টার বেইলির কাছে রেখে এসেছি। এরপরই একটু কষ্ট করে চেভি চেস কান্ট্রি ক্লাবে কল করে সেক্রেটারির কাছে একটা খবর পাঠাবে। আগামী হপ্তায় টেনিস টুর্নামেন্টে কিছুতেই অংশ নিতে পারছি না। আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিও-মনে হয় আমাকে ধরেই হিসাব করবে ওরা। তারপর ডাউন টাউন ইলেক্ট্রনিক্সে ফোন করে বলবে তারা যদি আমার স্টাডি রুমের ভিডিওটা আগামী হপ্তার…হ্যাঁ, বুধবারের মধ্যে ঠিকঠাক না করে তো আমি অর্ডার বাতিল করে ঐ নষ্ট জিনিসটা ফিরিয়ে আনব।’ একটু পজ বাটন চেপে সে মনে করার চেষ্টা করে আর কী কী সমস্যা হতে পারে সে এ কদিন পৃথিবীতে না থাকলে। সাথে সাথে দমও নিয়ে নেয়ু একটু।
‘টাকা পয়সায় টানাটানি পড়লেই অফিসে কল করো। তারা আমাকে জরুরী কল করতেও পারে, আমার জবাব দেবার মতো সময় থাকবে না। বাচ্চাদের আমার ভালবাসা জানিয়ে বলো যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসছি। ওহ! ধ্যাৎ-আশপাশে এমন একজন আছে যার সাথে আমি কথা বলতে চাই না-পারলে চাঁদ থেকে কল করব-গুড বাই।’
ফ্লয়েড কোনোমতে নিজেকে বুখ থেকে টেনে বের করার চেষ্টা করলো, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। এরই মধ্যে থামিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। সোভিয়েত বুথ থেকে মূর্তিমান আতঙ্কের মতো উদিত হয়েছে ইউ এস এস আর একাডেমি অব সায়েন্সের ডক্টর দিমিত্রি ময়শেভিচ।
দিমিত্রি ফ্রয়েডের বেস্ট ফ্রেন্ডদের একজন; আর সেই বিশেষ কারণেই দিমিত্রি শুধু তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তার খা বলতে হবে। এখন, এখানে।
অধ্যায় ৯. চান্দ্র যান
বিশালদেহী, পাতলা রাশিয়ান এ বিজ্ঞানী হালকা চুলের অধিকারী। তার রেখাহীন মুখমণ্ডল দেখে কেউ বলবে না বয়সে সে পঞ্চান্ন বছর পেরিয়েছে।
তার মধ্যে শেষ দশটা বছর কাটলো চাঁদের অপর পিঠে দৈত্যাকার রেডিও অবজার্ভেটরিং তৈরির কাজে। সেখানে দু-হাজার মাইল বিস্তৃত পাথর অবজার্ভেটরিটাকে পৃথিবীর শব্দ-আবর্জনা থেকে রক্ষা করবে।
‘তাইতো সব সময় বলি, ফ্লয়েড’, উষ্ণভাবে হাত আঁকাতে ঝাঁকাতে বলে গেল সে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা একদম ছোট। তা কেমন আছ তুমি? আর তোমার মিষ্টি বাচ্চাকাচ্চার খবর কী?
‘আমরা ভালই আছি। যথাসম্ভব উষ্ণভাবে জবাব দেয় ফ্লয়েড, গত গ্রীষ্মে তুমি আমাদের দারুণ সঙ্গ দিয়েছিলে। সেসব নিয়ে আজো কথা হয়। সে অপ্রস্তুত ভাব ঢাকার চেষ্টা করছে। গত গ্রীষ্মে আসলেই দিমিত্রির সাথে তাদের একটা উইক এন্ড কেটেছিল ভালোভাবে। রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা তখন ছুটিতে এসেছিল পৃথিবীর বুকে।
দিমিত্রি খোঁজখবর নেয়, আর যতটুকু মনে হচ্ছে, তুমি উপরের পথে, ঠিক?
‘ধ্যাৎ…হ্যাঁ-আধঘণ্টার মধ্যেই আমার ফ্লাইট ছেড়ে যাবে।’ জবাব দেয় ফ্লয়েড আমতা আমতা করে, তুমি কি মিস্টার মিলারকে চেন?
এরমধ্যেই সিকিউরিটি অফিসার এসে গেছে, একটু সম্মানসূচক দূরত্ব বজায় রেখেছে সসম্ভ্রমে। হাতে একটা কফির প্লাস্টিক কাপ।
‘অবশ্যই চিনি। কিন্তু প্লিজ কফির কাপটা নামিয়ে রাখুন। এটাই ডক্টর ফ্লয়েডের সভ্য ড্রিঙ্ক নেয়ার শেষ সুযোগ-নষ্ট না করাই ভালো সুযোগটা। চল ফ্লয়েড, একটা ড্রিঙ্ক… না-আমি অনুরোধ করছি…’।
অগত্যা তারা দুজনেই দিমিত্রির পিছু নেয় অবজার্ভেশন সেকশনের দিকে একটু পরেই তারা বসে ছিল এক মনোহর হাল্কা আলোর নিচে; দেখছিল দিগন্তজোড়া নক্ষত্রলোক। স্পেস স্টেশন ওয়ান প্রতি মিনিটে একবার গোত্তা খায় আর কেন্দ্রমুখী বলটা এই ঘূর্ণনেরই ফসল। বলের মান চাঁদের আকর্ষণের মানের কাছাকাছি। পার্থিব অভিকর্ষ একেবারেই না থাকার চেয়ে এটুকু থাকা ভালো। বরং লোকজনকে চাঁদে যাওয়ার আগে এক-আধটু চান্দ্রসুখ দেয়া যায়।
বাইরের একদম অদৃশ্য জানালা দিয়ে পৃথিবী আর তারকারাজির নিরব মহামিছিল দেখা যায়। এ মুহূর্তে সেকশনটা সূর্যের ঠিক উল্টোমুখো হয়ে থাকায় বাইরে দৃষ্টিক্ষেপের স্পর্ধা দেখানো যাচ্ছে, নইলে আলোর তোড়ে কোথায় ভেসে যেত জায়গাটা! এমনকি এখনো পৃথিবী-গোলকটা ভরে রেখেছে অর্ধাকাশ। সব ডুবে আছে অমানিশায়, শুধু মিটমিট করে উপস্থিতি জানিয়ে যায় তারার দল।
আসলে পৃথিবী প্রতীক্ষারত, এ অংশে এইমাত্র প্রবেশ করল স্টেশন ওয়ান। আরেকটু পরে রাতের দিকে গেলেই দেখতে পাবে মহানগরীর আলোকমালা। আর তখন পুরো আকাশই যেন চলে যাবে রাতের তারার দখলে।
‘তো, দ্রুত প্রথম দফা গলায় চালান করে দিয়ে দ্বিতীয়টার সাথে ক্রীড়ারত দিমিত্রি খেই ধরতে চাচ্ছে, চাঁদের ইউ এস সেক্টরে কীসের প্রাদুর্ভাব নিয়ে হৈচৈ চলছে? এবারের ট্রিপে যেতে চেয়েছিলাম, ‘নো, প্রফেসর।‘’ জবাব মিলল? ‘উই আর ভেরি স্যরি, কিন্তু পরের নোটিশ না আসা পর্যন্ত কড়া নিরাপত্তা বহাল রয়েছে।’ ক্ষেপে গিয়ে তার ধরে টানাটানি করেছিলাম, কারণ সেটা কোনো কাজেই লাগতো না। তো, তুমিই বল, হচ্ছেটা কী?’
ভিতরে ভিতরে গড়গড় করে কী যেন বলল ফ্লয়েড। আবারও এসব কথা! যত জলদি মুন শাটলে সেঁধিয়ে যেতে পারি, ততই বাঁচোয়া।
‘এই-এহ্-কোয়ারেন্টাইন একদমই নিরাপত্তার পদক্ষেপ।’ অতি সাবধানে বেচারা বলে চলে, আমরা ঠিক শিওর না এর দরকার আছে, নাকি নেই। কিন্তু ঝুঁকি নিতে নারাজ। এই আর কী!’
‘কিন্তু রোগটা কী? এর লক্ষণটক্ষণ? অপার্থিব নয়তো? আমাদের মেডিক্যাল সার্ভিসের একবিন্দু দরকার থাকলেও বলতে পার।’
‘আই এ্যাম স্যরি, দিমিত্রি-এ মুহূর্তে টু শব্দটাও করতে পারব না আমরা। অফারের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু নিজেরাই পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে পারব।’
‘হুমম্’ একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে বলল ময়শেভিচ, ‘আমার চোখে একদম বেমানান ঠেকে যে তুমি, একজন অ্যাস্ট্রোনমার হয়েও চাঁদে চলে যাচ্ছ একটা মহামারীর দেখভাল করতে।’
‘আমি শুধুই একজন প্রাক্তন জ্যোতির্বিদ, বা মহাকাশবিজ্ঞানী, যাই বলনা কেন। অনেক বছর ধরে কোনো রিসার্চ করি না। এখন শুধুই একজন সায়েন্টিফিক এক্সপার্ট, তার মানে হচ্ছে, আমি কোনোকিছুরই পুরোপুরি সবটুকু জানি না।’
‘তার মানে, তুমি হয়তো টি এম এ-১ নিয়েও তেমন কিছু জান না, জান কী?’
মনে হচ্ছে যেন মিলার নিজের ড্রিঙ্কে এক্কেবারে চুর হয়ে গেছে, জগতের কোনো কথাতেই তার কান নেই। কিন্তু ফ্লয়েড নিতান্তই কঠিন চিজ। সে নিজের পুরনো দোস্তের দিকে চোখে চোখে তাকায়, বরফশীতল নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, ‘টি এম এ-১? কী অদ্ভুত নামরে বাবা! কোথায় শুনলে এসব?
‘নেভার মাইন্ড।’ জবাব ছেড়ে রাশিয়ান, ‘আমাকে বোকা বানাতে পারবে না তুমি। কিন্তু তোমরা যদি এমন কিছু নিয়ে মেতে থাক যা আর সামলে উঠতে পারছ না, আশা করি সেটা সামলেসুমলে উঠতে গিয়ে এত দেরি করে বসবে না যাতে হল্লা করে মরতে হয় ‘হেল্প! হেল্প!’ বলে।’
মিলার অর্থপূর্ণভাবে নিজের ঘড়ির দিকে তাকায়।
‘আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ছাড়ছে ডক্টর ফ্লয়েড। মনে হয় এখনি যাওয়া ভালো।’
যদিও সে জানে হাতে জলজ্যান্ত বিশটা মিনিট পড়ে আছে, তবু তোণ্ডতি করে উঠে পড়ে। এত বেশি ব্যস্ত দেখায় যে গ্র্যাভিটির ছ’ভাগের একভাগের কথাটা মনেই পড়ে না। উড়ে যাওয়া ঠেকাতে সময়মতো টেবিলটা খপ করে ধরে নিয়ে নিজেকে সামলায়।
‘তোমার সাথে দেখা হওয়ায় দারুণ লাগল, দিমিত্রি।’ কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়, ‘আশা করি পৃথিবীতে দারুণ এক ভ্রমণ শেষে ফিরবে-ফিরে এলেই একটা কল দেব তোমাকে।’
লাউঞ্জ ছেড়ে ইউ এস ট্রানজিট ব্যারিয়ারে গিয়েই ফ্লয়েড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, ‘ফুহ-কানের পাশ দিয়ে গুলি গেল। আমাকে সময়মতো উদ্ধার করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।
‘জানেন, ডক্টর,’ সিকিউরিটি অফিসার হালকা লয়ে বলে, ‘আশা করি তার কথাটা ঠিক না।’
‘কোন্ কথাটা?’
‘সামলে উঠতে পারি না এমন কিছুতে হাত দেয়া না কী যেন বললেন তিনি…’
‘ঠিক’ বলে ওঠে ফ্লয়েড, এই ব্যাপারটা দেখতেই আমি যাচ্ছি।’
পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে এ্যারেস ওয়ান বি লুনার ক্যারিয়ার স্টেশন থেকে ভেসে ওঠে। পৃথিবী থেকে টেক অফের মতো ঝক্কি ঝামেলার কোনোটাই এখানে নেই-শুধু লো ব্রাস্টের একটা প্রায় শ্রবণসীমার নিচের দূরাগত শব্দ। লো থ্রাস্ট প্লাজমা জেটগুলো মহাকাশে তাদের তড়িত্বন্যা বইয়ে দিলেই এমন শব্দ ওঠে। হালকা ধাক্কা চলে মিনিট পনের ধরে, তারপরের মৃদু গতিবৃদ্ধি কাউকেই নিজের ভেসে বেড়ানো থেকে বিরত করেনি। এবার আর যানটা বাঁধা পড়ে নেই পৃথিবীর মায়াজালে। এটা আর স্পেস স্টেশন বা চাঁদের মতো কোনো উপগ্রহ নয়। এ্যারেস ওয়ান বি’র উপর পার্থিব কোনো বল কাজ করছে না বলেই এখন এ এক মুক্ত গ্রহ।
ফ্লয়েড একা যে কেবিন জুড়ে বসেছে সেটা আসলে ত্রিশজনের জন্য বানানো। চারদিকের খালি খালি সিট দেখতে অদ্ভুত লাগে, ভর করে একাকিত্ব। বেশি বিরক্তিকর ব্যাপার হল, ত্রিশজন অতি দামী, অতি সম্মানিত এবং কিছু ক্ষেত্রে অতি খরুচে যাত্রীর জন্য যথেষ্ট যে স্টুয়ার্ড আর স্টুয়ার্ডেস, তাদের সবার কাজের এবং মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে সে। পাইলট, কো পাইলট আর দুই ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলতে হয় না। বড়ই সন্দেহ তার, ইতিহাসে আর কোনো মানবসন্তান এত বেশি এক্সক্লসিভ সার্ভিস পেয়েছে কিনা; আর ভবিষ্যতে কারো পাওয়ার আশা তো আরো কষ্টকল্পনা। তার অকস্মাৎ মনে পড়ে যায় কোনো এক অনুল্লেখ্য ধর্মগুরুর কথা, এবার যখন পোপত্ব পেয়েই গেলাম, চলো, উপভোগ করি ব্যাপারটা। যাক, সেও এ ট্রিপ আর ওজনহীনতার চরম আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ওজনহীনতা মুহূর্তের জন্যে হলেও তার সচেতনতাকে ঢেকে ফেলে। কে যেন একবার বলেছিল, আপনি স্পেসে আতঙ্কে অস্থির হতে পারেন, কিন্তু একবিন্দু দুঃখও পেতে পারেন না। একদম খাঁটি কথা।
দেখেশুনে মনে হচ্ছে স্টুয়ার্ড বেচারা ট্রিপের পুরো পঁচিশ ঘন্টা জুড়েই তাকে খাইয়ে যাবার পণ করেছে। ফ্লয়েড ক্রমাগত ফিরিয়ে দিচ্ছে একের পর এক খাবার। এখন আর জিরো গ্র্যাভিটিতে খাওয়াদাওয়াটা কোনো সমস্যাই নয়, আঁধারে হারিয়ে যাওয়া সাবেক অ্যাস্ট্রোনটদের কথা অবশ্য পুরো বিপরীত। সে একটা সাদামাটা টেবিলের সামনে বসেছে, সেটায় সেঁটে দেয়া হয় খাবারের প্লেটগুলো-যেন সে বসে রয়েছে উত্তাল সাগরের টালমাটাল কোনো জাহাজের ডেকে। প্রতিটা জিনিসই সেঁটে থাকে, যাতে কেবিনজুড়ে বিশ্রী ওড়াউড়ি ঠেকানো যায়। যেমন, একটা চপ আটকে থাকে আঠালো সসের সাথে, বা কোনো সালাদের প্রিপারেশনের সাথে থাকবে থকথকে কোনো না কোনো তরল। আসলে একটু সতর্ক থাকলে সবই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিষিদ্ধ খাবারের মধ্যে আছে গরম গরম স্যুপ আর একদম ভঙ্গুর পেস্ট্রি। ড্রিঙ্কের ব্যাপারে পরিস্থিতি একটু ভিন্ন, সব তরলই খেতে হয় প্লাস্টিকের স্কুইজ বোতলে করে।
ওয়াশরুমের ডিজাইনের পেছনে পুরো একটা প্রজন্মের ‘মহান’ স্বেচ্ছাশ্রম ব্যয় হয়েছে। কিন্তু কেউ এ মহত্ত্ব নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করে না। আজ এ রুমটা কমবেশি ‘পরিণত’ হিসেবে বিবেচিত। মুক্ত পতন শুরুর পরপরই এর খোঁজখবর নেয় ফ্লয়েড। নিজেকে আবিষ্কার করে একটা সাধারণ বিমান-ওয়াশরুমের মতো দেখতে একটা কিউবিকলে। শুধু একটা জিনিসই নিষ্ঠুরভাবে জুলজুল করছে চোখের উপর। লাল আলোতে বড় বড় অক্ষরে লেখা, ‘সবচে গুরুত্বপূর্ণ! আপনার নিজের আরামের জন্য এই ইট্রাকশনগুলো পড়ে নিন প্লিজ!’
ফ্লয়েড বসে নেয় (ওজনহীনতায়ও মানুষ ভুলে বসে পরে) তারপর পড়ে নেয় কয়েকবার। আগের ট্রিপের পর কোনো পরিবর্তন আসেনি বুঝতে পেরেই চেপে দেয় স্টার্ট বাটন।
হাতের কাছাকাছি একটা ইলেক্ট্রিক মোটর বনবনিয়ে ঘুরছে। ফ্লয়েড নিজেকে আবিষ্কার করে ঘুরন্ত অবস্থায়। নোটিশের উপদেশ মতো সে চোখ বন্ধ করে রাখে কিছুক্ষণ। মিনিটখানেক পরেই একটা বেল বেজে উঠলে চারপাশে তাকায় সে।
এবার আলো নিখাদ গোলাপি-সাদায় বদলে গেছে। তারচেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার-সে গ্র্যাভিটি ফিরে পেয়েছে। একদম মৃদু কাপনেই শুধু বোঝা যায় যে অভিকর্ষটা কৃত্রিম। পুরো টয়লেট কম্পার্টমেন্ট করোসেলের মতো ঘুরছে। এক টুকরো সাবান তুলে নেয় ফ্লয়েড, তারপর ধীরে এটার পড়ে যাওয়া দেখতে পায়। সে নিশ্চিত হয়ে নিল যে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স সাধারণ গ্র্যাভিটির অন্তত চারভাগের একভাগ হয়েছে। এই যথেষ্ট। বোঝা যাচ্ছে অন্তত যেখানে ঠিকমতো চলাটা জরুরী সেখানে সব চলছে ঠিকঠাক।
সে ‘স্টপ ফর এক্সিট’ বাটনটা চেপে ধরেই আবার বন্ধ করে চোখ। ঘুর্ণন কমার সাথে সাথে ওজন আবার পালিয়ে যাচ্ছে। বেলটা দুবার বেজে উঠতেই লাল ওয়ার্নিং বাতি জ্বলে ওঠে। দরজাটা ঠিক জায়গামতো লক হয়ে যায়। এবার ঠিকমতো ভেসে বেরুনো যাবে। কেবিনে ঢুকেই সে নিজেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আটকে নেয় কার্পেটের সাথে। বহুকাল আগেই সে ওজনহীনতার মহত্ত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। আজ আর অভিকর্ষহীনতা মজার কোনো অভিজ্ঞতা নয়, বরং তার কাছে ভেলক্রো চপ্পল এক প্রকার আশীর্বাদ।
সময় কাটানোর অনেক ব্যবস্থাই আছে। এমনকি বসে বসে পড়লেও সময় কেটে যেতে পারে। অফিসিয়াল রিপোর্ট আর মেমোরেন্ডার দঙ্গল দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে পড়লেই সে নিজের ফুলস্কেপ কাগজ গড়নের নিউজপ্যাডটাকে শিপের ইনফরমেশন সার্কিটের সাথে যুক্ত করে নেয়। চোখ বুলিয়ে নেয় পৃথিবীর সর্বশেষ খবরগুলোয়। একের পর এক পৃথিবীর তাবৎ বড় পত্রিকা তুলে আনে। গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রিক নিউজপেপারগুলোর কোডও আর মুখস্ত। প্যাডের পেছন থেকে দেখে নিতে হয় না। ডিসপ্লে ইউনিটের শর্ট টার্ম মেমোরিতে সুইচ করেই প্রথম পাতাটা পাওয়া যায়। সাথে সাথেই কৌতূহলোদ্দীপক হেডলাইনগুলো নোট করে নিচ্ছে। প্রতিটির আছে দু’ডিজিটের ভিন্ন রেফারেন্স নাম্বার। ডিজিট চাপলেই পোস্টেজ-স্ট্যাম্প আকারের ছোট্ট চতুষ্কোণ খবরটা প্রসারিত হতে হতে প্রায় পুরো নিউজপ্যাড ভরে তোলে, যাতে আয়েশ করে পড়া যায়। পড়া শেষ হতেই চলে যাওয়া যায় পুরো পাতায়, তারপর বাকী থাকে প্রয়োজনমাফিক অন্য কোনো বিষয় বেছে নেয়া।
মাঝে মধ্যেই ফ্লয়েড বেশ ধাঁধায় পড়ে যায়, কে জানে-নিউজপ্যাড আর এর পেছনের টেকনোলজিই মানব সভ্যতার যোগাযোগের শেষ ও পরিপূর্ণ পরিণতি কিনা! এইতো, সে বেরিয়ে পড়েছে অসীম স্পেসের বুকে; মৃত্তিকা থেকে সরে যাচ্ছে প্রতি ঘন্টায় কত সহস্র মাইল দূরে-এখনো চাওয়ামাত্র যে কোনো খবরের কাগজের হেডলাইন দেখতে পায় কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে। (‘খবরের কাগজ’ শব্দটা নিশ্চয়ই আধুনিক ইলেক্ট্রনিক যুগের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া সিন্দাবাদের ভূত! এ নামের অস্তিত্ব শুধু অতীতেই ছিল, ব্যবহার বর্তমানে।) প্রতি ঘন্টায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য নবায়ন করা হয়। কেউ যদি শুধু ইংরেজি খবরগুলোই পড়তে থাকে, তবু নিউজ স্যাটেলাইটগুলো থেকে আসতে থাকা চির পরিবর্তনশীল সংবাদ প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে একটা পূর্ণ জীবন পার করে দিতে পারে সহজেই।
কী করে যে পুরো সিস্টেমটা অটোম্যাটিক আপগ্রেড হয় তা ভেবেই কুল কিনারা পায় না সে। কিন্তু আজ হোক আর কাল, ফ্লয়েড জানে, এটাও ভেসে যাবে প্রযুক্তির বাধাহীন তোড়ে। এমন অকল্পনীয় কিছু সিন্দাবাদের ভূতের দায়িত্ব নেবে, যা ভাবতেও বিষম খেতে হয়। সেদিনও হয়তো এর নাম থাকবে ‘নিউজপেপার’! কক্সটন বা গুটেনবার্গ কোনোদিন কি নিউজপ্যাড স্বপ্নেও দেখেছিলেন?
আরো একটা ব্যাপার যেন ধরা দেয় ঐ ছোট্ট নিউজগুলোয়। দিনকে দিন যোগাযোগ মাধ্যম যতই চমৎকার হচ্ছে, ততই যেন সাধারণ, সস্তা আর হতাশাজনক হয়ে পড়ছে এর উপাদানগুলো। অ্যাক্সিডেন্ট, অপরাধ, প্রাকৃতিক আর মানবসৃষ্ট বিপর্যয়, যুদ্ধের হুমকি-ধামকি, নীরস সম্পাদকীয়-এসবই যেন ইথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীময় ছড়ানো লাখো শব্দের মূল লক্ষ্য। অবশ্য আজো ফ্লয়েড নিশ্চিত হতে পারেনি ব্যাপারটা খুব খারাপ হল কিনা। ইউটোপিয়ার সংবাদপত্রগুলো অসম্ভব মলিন আর বিরক্তিকর দেখাবে নিশ্চয়ই।
কিছুক্ষণ পরপরই কেবিন ক্রু আর ক্যাপ্টেন কেবিনে একটু ঢু মেরে যায়। কথাও হয় দু-চারটি। তারা অতি আগ্রহের সাথে তাদের বিশিষ্ট যাত্রীর সাথে কথা বলে। তবে মজার ব্যাপার হল, কথা বলায় শিষ্টতা রক্ষার চেয়ে তাদের গোপন মিশনের ব্যাপারে ব্যাকুলতাই বেশি ধরা পড়ছে। তবে বাঁচোয়া, তারা যথেষ্ট ভদ্র, একটা কথা তো দূরে থাক, এ বিষয়ে এক বিন্দু ইশারাও করে না।
একমাত্র কমবয়েসী মিষ্টি স্টুয়ার্ডেসকেই তার উপস্থিতিতে একদম স্বচ্ছন্দ মনে হয়। হঠাৎ ফ্লয়েড আবিষ্কার করে বসে, মেয়েটা এসেছে বালি[১৯] থেকে। বোঝা যায়, সে আজো বহন করে চলেছে সেই পরিবেশের মধুর রহস্যময়তা। আজো বিশাল এ দ্বীপ নষ্ট হয়ে যায়নি, হারায়নি তার দারুণ সৌন্দর্য। তার অবাক লাগে, এই পুরো ট্রিপের মধ্যে সবচে ভালো লেগেছে জিরো গ্র্যাভিটির কিছু অনিন্দ্যসুন্দর ব্যালে নৃতের মহড়া। মেয়েটা নিশ্চয়ই নাচছে না, কিন্তু দেখে তেমন মনে হয়। পেছনে নীলচে পৃথিবীর যবনিকা।
নিভে গেছে কেবিন লাইট। ঘুমানোর সময় ইলাস্টিক স্ট্র্যাপে নিজের হাত-পা আটকে নেয় ফ্লয়েড। ঘুমের মধ্যে এদিকসেদিক ভাসতে হবে না আর। একটু বেখাপ্পা দেখালেও এটাই রীতি। ফ্লয়েডের কাউচটা পৃথিবীর যে কোনো ম্যাট্রেসের চেয়ে অনেক বেশি আরামদায়ক।
নিজের ভিতর ডুবে যাবার পর অর্ধসচেতনভাবে জেগে উঠে সে বেশ বিপাকে পড়ে যায়। আশপাশটা দেখে চিনতে পারেনি প্রথমে। একপলের জন্য মনে হয় সে শুয়ে আছে কোনো টিমটিমে চাইনিজ লণ্ঠনের ভিতরে। আশপাশের কিউবিকল থেকে আসা ক্ষীণ আলোকমালায় এমনটা মনে হতেই পারে। এরপর নিজেকে শুনিয়ে বলে চলে, ‘ঘুমাও, ছেলে। এ এক সাধারণ মুন শাটল।’
জেগে উঠে সে আধ আকাশের অধীশ্বর চাঁদকে দেখতে পায়। ব্রেকিং প্রকৌশল শুরু হবে এখুনি। প্যাসেঞ্জার সেকশনের বাঁকানো দেয়ালে বিশাল জানালার এক বৃত্তচাপ আছে। সেটা দিয়ে এবার আর এগুতে থাকা গ্লোবের দেখা পাওয়া যাবে না। দেখা যাবে আকাশ। তাতে কী, রিয়ারভিউ টিভিতে ভালোভাবেই চূড়ান্ত পর্যায় দেখা যায়। টিভি স্ক্রিনটা কন্ট্রোল কেবিনে, অগত্যা তার সেদিকে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।
আসতে থাকা চান্দ্র পাহাড়গুলো পৃথিবীর পাহাড় থেকে অনেক অনেক ব্যতিক্রমী। তাদের নেই পার্থিব পর্বতের তুষারশুভ্র টুপি, নেই সবুজের ছড়াছড়ি। উদ্ভিদজগতের অনিন্দ্যসুন্দর আটসাট পোশাক নেই তাদের, নেই মেঘরূপী সদাচলন্ত কিরিটী। মেঘ-মুকুট ছাড়া কোনো পাহাড়কে কি সম্রাট মনে হয়?
তাতে কী? তাদের অবাক করা আলো আঁধারের সৌন্দর্যটাতো একান্তই নিজস্ব। দুনিয়াব্যাপী সৌন্দর্যের সংজ্ঞাগুলো এখানে অসহায়। এ ভুবন গড়ে উঠেছে আরেক শক্তিতে। সময়ের অনন্ততার উপর এর ভিত, কোনো অর্বাচীন একে বুঝে উঠতে পারবে না এক লহমায়। প্রতিনিয়ত নতুন রূপ নেয়া শ্যামল পৃথিবী তার ভেসে চলা বরফ যুগ, তার সদাচঞ্চল সাগর আর সূর্যোদয়ের আগের ধোঁয়াশার মতো পাহাড় নিয়ে এই অসীমের স্পর্শ পেতে পারবে না। এখানে একটাই যুগ, অসীম, অস্পৃশ্য, অনন্ত। একে মৃত্যু বলা যায় না, কারণ শশী কখনোই জীবিত ছিল না। অন্তত আজ পর্যন্ত এটাই সত্যি।
দিন আর রাতের স্থির রেখার ভিতর নেমে আসছে শিপটা। নিচে আলো আঁধারীর মিশেল, অতি ধীর চান্দ্র সূর্যোদয়ের প্রথম কিরণের স্পর্শ পায় নিঃসঙ্গ চূড়াগুলো। সবচে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়েও এখানে ল্যান্ড করাটা ভয়ংকর হওয়ার কথা। ধীরে সরে গেল এলাকাটা, এগিয়ে আসছে রাতের পাশ।
একেবারে ক্ষীণতম আলোর সাথে চোখ সয়ে এলে ফ্লয়েড দেখতে পায় ফ্লাইটের ল্যান্ডিং এলাকা একেবারে আলোকহীন নয়। এক ভৌতিক বিচ্ছুরণে আলোকিত হয়ে আছে আশপাশটা। চূড়া, পাথর আর সমতল দেখা যাচ্ছিল একেবারে স্পষ্ট। চাঁদের আকাশেও আছে এক দানবাকার চাঁদ। পৃথিবীর আলো এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে চতুর্দিক।
পাইলট প্যানেলের রাডার স্ক্রিনে আলো খেলে খেলে যায়। কম্পিউটার ডিসপ্লেতে সংখ্যা ওঠে অনেক, হারিয়েও যায় আবার। প্রতি পলে চাঁদের সাথে দূরত্ব মেপে চলছে যন্ত্রপাতি। প্রথম ওজন ফিরে আসার সময় চাঁদের ভূমি হাজার কিলোমিটার নিচে ছিল। আলতো একটু ঝাঁকি এল, তারপর নিচের দিকে সম্মোহন। যুগযুগ ধরে চেষ্টা করে যেন চাঁদটা পুরো আকাশ দখল করে নিল। কবেই ডুবে গেছে সূর্য, শেষে এক দানো শৃঙ্গ অধিকার করে নেয় বাকী আকাশটা।
শাটল যাচ্ছিল কেন্দ্রীয় চুড়ার দিকে। একেবারে অকস্মাৎ ফ্লয়েড আবিষ্কার করে বসে, সবচে কাছের শৃঙ্গটা থেকে আলো আসছে নিয়মিত ছন্দে। পৃথিবীর হিসাবে এ এক এয়ারপোর্ট বীকন। দম আটকানো দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ফ্লয়েড, মানুষ যে চাঁদে তার সর্বজয়ী পা রেখেছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ এ আলো।
এবার উঁচুভূমি এত বেশি এগিয়ে এসেছে যে দেখে মনে হতে পারে এর গিরিজ্বালামুখটা হাঁ করা; ছোটগুলো যেন সাজপোশাক, তীক্ষ্ণ পাথুরে অগ্রভাগগুলো উপরের দিকে চেয়ে আছে ব্যাকুলভাবে। এরা সবাই যেন নিজেদের আসল রূপ ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী। কোনো কোনোটা পুরো এক নগরীকে বুকে ধরার মতো মাইলের পর মাইল প্রান্তর জুড়ে আছে।
নক্ষত্রালোকে আলোকিত আকাশ থেকে পিছলে নামছে মুন শাটল। নিজের কাজের উপর এ যান পুরো কর্তৃত্ব রেখেছে। কেবিনের ভিতর ছুটতে থাকা ইলেক্ট্রনিক বীপিং আর জেটগুলোর তর্জন-গর্জন ছাপিয়ে কোত্থেকে যেন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ফ্লয়েড শুনতে পায় কণ্ঠের গুঞ্জন।
‘ক্ল্যাভিয়াস কন্ট্রোল থেকে স্পেশাল ফোর্টিনকে বলছি, এগিয়ে আসছেন দারুণভাবে। হাইড্রোলিক প্রেশার, শক প্যাড ইনফ্লেশন আর ল্যান্ডিং গিয়ার লকের উপর হাতেনাতে চেকিংটা সেরে ফেলুন প্লিজ।’
পাইলট সানড্রাই সুইচ চেপে ধরার পরই সবুজ বাতি জ্বলে ওঠে, সাথে সাথেই কলব্যাক পাঠায় দক্ষ নাবিক, ‘সব ম্যানুয়াল পরীক্ষণ শেষ। হাইড্রোলিক প্রেশার, শক প্যাড ইনফ্লেশন আর ল্যান্ডিং গিয়ার লক ঠিক আছে পুরোপুরি।’
‘কনফার্মড।’ বলল চাঁদ। বাকী কথা হারিয়ে গেল যেন। হ্যাঁ, আরো শত কথা বাকী, সেটা চলছে যন্ত্রপাতির সাথে। যন্ত্রগুলো ধীর মালিকদের চিন্তার চেয়ে সহস্রগুণ দ্রুতিতে বাইনারি সংকেত পাঠিয়ে চলছে অবিরত।
এর মাঝেই বেশকিছু মাউন্টেন পিক চান্দ্রযানের মাথার উপর থেকে উঁকি মারা শুরু করেছে। ভূমি আর মাত্র কয়েক হাজার ফুট নিচে। কয়েকটা নিচু বিল্ডিং আর কিম্ভুতকিমাকার যানবাহনের ভিড় ঠেলে দেখা দিচ্ছে বিশাল নক্ষত্রের মতো বিকন লাইটেরআলো। শেষ পর্যায়ে জেটগুলো যেন কোনো জটিল আর সূক্ষ্ম সুর তোলার চেষ্টায় রত। এমন সুরেই সেগুলো দিয়ে বেরুচ্ছে জ্বালানী। থ্রাস্টের সাথে শেষ মুহূর্তের কাজ চালানোর জন্যই এ কাজ।
এলোমেলোভাবে ধূলির এক ঝড় আশপাশটাকে ভরিয়ে তুলতে চাচ্ছে। জেটগুলো অন্তিম এক গর্জন দিয়ে শাটলকে আলতো হাতে চাঁদের বুকে নামিয়ে দিল। এত হালকাভাবে চান্দ্রযান নামল যেভাবে কোনো রাবারের নৌকা ছোট্ট ঢেউয়ের মুখে আন্দোলিত হয়। কয়েক মিনিট আগে হলেও এখনকার এ নিরবতাকে ফ্লয়েড মেনে নিতে পারত না, কিন্তু তার সাথে এবার হাল্কা অস্বস্তিকর গ্র্যাভিটিও মেনে নিতে হচ্ছে।
নিতান্তই আটপৌরে রুটিন ফ্লাইটের পর ডক্টর ফ্লয়েড পদার্পণ করে চির আকাক্ষিত চাঁদের বুকে। একেবারে নিরাপদে একদিনের একটু বেশি সময় নিয়ে শেষ করেছে সেই বুক কাঁপানো যাত্রা-যেটার আশায় সহস্র কোটি মানুষ দু-হাজার বছর ধরে ব্যাকুল ছিল। আসলেই কি মাত্র দু-হাজার বছর?
অধ্যায় ১০. ক্ল্যাভিয়াস বেস
ব্যাসে দেড়শো মাইল, ক্ল্যাভিয়াস, চাঁদের দেখা যাওয়া অর্ধাংশের দ্বিতীয় বড় জ্বালামুখ। অবস্থান দক্ষিণ চাঁদের উচ্চভূমিতে। খুবই পুরনো, শত বছর ধরে লাভার উদ্গীরণ হয়েছে, হাজার হাজার বছর ধরে এর শুকনো বুকে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে মহাকাশের আগন্তুকেরা। উল্কা, পাথর, কণা।
কিন্তু শিলাসৃষ্টির শেষ যুগ থেকেই এটা শান্ত। আজো অ্যাস্টেরয়েড বেল্টের ছোট্ট গ্রহাণুরা আঘাত হানে ভিতরের দিকের গ্রহগুলোয়, কিন্তু চাঁদের এ অংশ গত পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে ঘুমিয়ে আছে একদম।
আর আজ, এর ভিতরে বাইরে কী অদ্ভুত আলোড়ন! চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম স্থায়ী ফোস্কা পড়েছে ঠিক এখানটাতেই। বিশেষ প্রয়োজনে ক্ল্যাভিয়াস বেস স্বয়ং একটি পরিপূর্ণ দুনিয়া হয়ে উঠতে পারে। স্থানীয় পাথর থেকেই জীবনধারণের সবকিছু গড়ে ওঠে। শুধু দরকার ভাঙা, তাপ দেয়া, রাসায়নিক বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস থাকলে আর কী চাই! উপরি পাওনা হিসেবে জুটবে বাকী মৌলের বেশিরভাগ, শুধু জানা চাই কোথায় খুঁজতে হবে।
বেসটা এক ক্লোজড সিস্টেম; অভ্যন্তরীণ পরিবেশ-ব্যবস্থা। বসুন্ধরার এক ছোট্ট কর্মচঞ্চল মডেল যেন। এখানে জীবনের সবকিছুকেই রিসাইক্লিং করে নেয়া হয়। কোনো কিছুই ফেলা হয় না, সবকিছু থেকেই পুনরুৎপাদন। তারপর আবার, বারবার। বায়ুমণ্ডলটা পরিষ্কার করা হয় এক বিশাল ‘হটহাউস’-এ। এ এক বিরাট গোলাকার ঘর; অবস্থান চান্দ্র ভূমির নিচে। রাতে আশীর্বাদধন্য কৃত্রিম আলোকমালা আর দিনে ছেকে শুদ্ধ করা সূর্যালোক একরের পর একর এলাকাজুড়ে খাটো আর ঝাকড়া গাছের জীবন দিয়ে চলে। পরিবেশটা একদম উষ্ণ। সেগুলোর আছে অন্যরকম ক্ষমতা, আরো বেশি অক্সিজেন দেয়, পার্শ্ব ফলন হিসেবে খাদ্যতো আছেই।
বেশি খাদ্যোৎপাদনের জন্য কেমিক্যাল প্রসেসিং সিস্টেম আর অ্যালগি[২০] কালচারের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা হয়। বেসের চারদিকে স্বচ্ছ প্লাস্টিক : টিউবগুলোর বিস্তৃত এলাকার ভিতরে গজিয়ে ওঠা অজস্র আগাছা একেবারে হেলায় ফেলে রাখা হচ্ছে, কারণ খাদ্য সংকট নেই। প্রয়োজন পড়লেই একজন বায়োকেমিস্ট এ থেকে এমন চপ আর সুস্বাদু সজি গড়ে তুলতে পারে যার সাথে আসল খাবারের পার্থক্য নিতান্ত অভিজ্ঞজন ছাড়া কেউ আদৌ বুঝবে না।
বেসের এগারোশ পুরুষ আর ছ’শ মহিলার সবাই সর্বোচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী নয়তো টেকনিশিয়ান। পৃথিবী ছাড়ার আগে তাদেরকে হাজার সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা হয়েছে। আজ লুনার বেস বলতে গেলে একদম সহজ পরিশ্রমের স্থান। আজ আর প্রাথমিক সময়ের মতো অসুবিধা, দুর্ঘটনা কিংবা অঘটন ঘটে না। কিন্তু ভয় রয়েই গেছে, সামান্যতম ক্ল্যাস্ট্রোফোবিয়ায় ভোগা মানুষও এখানে কাজে আসার অনুমতি পায় না। একেবারে নিরেট পাথর আর লাভা কেটে কেটে চাঁদের বুকে ঘাটি পাতা নিতান্তই খরুচে ব্যাপার ছিল, সময়ও লেগেছে খুব বেশি। তাই এখানে একটা ভালো ‘ওয়ান-ম্যান’ রুম মাত্র ছ’ফুট চওড়া, দশফুট লম্বা আর উচ্চতায় আট।
প্রতিটিই আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো, দেখতে যে কোনো ভালো মোটেল স্যুটের মতোই। কনভার্টেবল সোফা, টিভি, ছোট্ট হাই-ফাই সেট আর ভিশন ফোন এর অংশ। একটু কৌশল করে একেবারে চোখের সামনে সেঁটে থাকা দেয়ালটাও কাজে লাগিয়ে ফেলা হয়েছে, পার্থিব বিশাল আটটি ছবি চারদেয়ালে ফুটিয়ে তোলা যায়। এত বিলাস খুবই প্রয়োজন বেসের জন্য, কিন্তু তারপরও পৃথিবীতে ব্যাখ্যা পাঠাতে হয় প্রতিনিয়ত। ক্ল্যাভিয়াসের প্রত্যেক নারী-পুরুষের পেছনেই ট্রেনিং, যাতায়াত আর বাসার জন্য শতসহস্র ডলার খরচ হয়; তাই তাদের মনের শান্তি আর ভারসাম্য রক্ষার পেছনে একটু ব্যয় করাই যায়। এ শিল্পের খাতিরে শিল্প নয়, সুস্থতার খাতিরে শিল্প।
বেস-বিশেষ করে সমগ্র চাঁদে বাসের জন্যই এক বিশাল সুবিধা পাওয়া যায়, কম মধ্যাকর্ষণ। এর ফলে এক অদ্ভুত ভালো থাকার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মধ্যে। এর নিষ্ঠুর দিকও আছে, চাঁদের একজন ইমিগ্র্যান্টের জন্য পৃথিবীতে থাকা অভ্যাস করে নিতে বেশ কয়েক হপ্তা লেগে যায়। চাঁদের বুকে মানবদেহ পুরো নতুন এক নির্ভরশীলতা নিয়ে গড়ে ওঠে। প্রথমবারের মতো মানুষের শরীরকে ভর আর ওজনের সামঞ্জস্য ঠিক করে নিতে হচ্ছে।
যে লোক পৃথিবীতে একশো আশি পাউন্ড শরীর বয়ে বেড়াত সে চাঁদে ত্রিশ পাউন্ডের ফুরফুরে স্বাস্থ্য নিয়ে চলতে শান্তি পাবে অবশ্যই। যখনি বরাবর চলবে, তখনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। বিপদ দেখা দেয় পাশ ফিরতে নিলেই। হঠাৎই বেচারার আবিষ্কার করতে হবে নিজের একশো আশি পাউন্ডের সবটুকুই বল আকারে ফিরে এসেছে। কারণ এ একটা ব্যাপার সব, স-ব জায়গায় একই, তা, সেটা হোক পৃথিবী, চাঁদ বা স্পেস। একটা ব্যাপারের সাথে অভ্যস্ত হতেই হবে, তাদের ওজনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার তুলনায় সবকিছু ছ’ভাগের একভাগ ধীর হয়ে গেছে। ভরবেগই এর কারণ। এ সমস্যায় পড়তেই হয়। কারো ঘাড়ে গিয়ে পড়া, কারো সাথে রামধাক্কা খাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।
নিজের জটিল ও একাধিক ওয়ার্কশপ, অফিস, স্টোররুম, কম্পিউটার সেন্টার, জেনারেটর, গ্যারেজ, রান্নাঘর, ল্যাবরেটরি, ফুড প্রসেসিং প্ল্যান্ট নিয়ে ক্ল্যাভিয়াস একাই এক বিশ্ব। আর, সত্যি বলতে গেলে, এই আন্ডারগ্রাউন্ড সাম্রাজ্য গড়তে যে দক্ষতার প্রয়োজন পড়েছে তার অনেকগুলোই অর্জিত হয়েছে স্নায়ুযুদ্ধের পঞ্চাশ বছরে।
মিসাইল সাইটে কাজ করা যে কেউ ক্ল্যাভিয়াসে স্বস্তি বোধ করবে। এখানে, এই চাঁদের বুকের ভিতরও কাছাকাছি দৃশ্য দেখা যায়, একই কায়দার যন্ত্রপাতি, একই ছাঁচের জীবন পদ্ধতি, একইভাবে বিরূপ পরিবেশের মোকাবেলা, মাটির নিচের ছোট্ট পরিবেশে বসবাস। পার্থক্য একটাই, এটাই টেনে দেয় যবনিকা, এ স্থান শান্তির জন্যে বানানো। দশ হাজার বছর পর মানুষ যুদ্ধের মতো উত্তেজক অন্য কোনো কাজ পেল।
আফসোস, আজো বাকী বিশ্বের সবগুলো দেশ এ সত্য অনুধাবন করতে পারল না।
.
ল্যান্ডিংয়ের একটু আগেও যেসব দানব-দানব পাহাড় দেখা যাচ্ছিল চারদিক থেকে সেগুলো ভোজবাজির মতো উবে গেছে, তাদের নামগন্ধও নেই। চান্দ্র দিগন্ত খুব দ্রুত আকাশের সাথে মিশে যায় বলে দেখা যাচ্ছে না। স্পেসক্রাফটের চারপাশে একটা সমতল, ধূসর এবং আলোকোজ্জ্বল এলাকা। আকাশটা অবশ্যই পুরোপুরি কালো। শুধু উজ্জ্বল তারা আর কিছু গ্রহ চোখে পড়ে। আকাশের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না, চোখ ঝলসে ওঠে চান্দ্রভূমির আলোয়।
অ্যারেস ওয়ান-বি স্পেসশিপের আশপাশে বেশকিছু কিম্ভুত যানবাহন ভিড় করেছে। কয়েকটা স্বয়ংক্রিয় আর বাকীগুলো চালায় ছোট্ট প্রেশার কেবিনে বসে থাকা অপারেটর। ভেহিকলগুলোর বেশিরভাগই চলে বেলুন-চাকায়, কারণ এভাবেই উঁচুনিচু ভূমিতে কেবিনের ভারসাম্য রক্ষা হয়। এখানটা সমতল হলেও বাকী চাঁদতে তেমন নয়।
যানগুলোয় সমতল বেশ কিছু প্লেট চারদিকে বৃত্তাকারে থাকে। প্রতিটি আলাদাভাবে বসানো, নিখুঁতভাবে সাজানো। আর আছে ফ্লেক্স হুইল, এতে ক্যাটারপিলার ট্রাকের প্রায়
সব গুণই ধরা দেয়, তবে আরেকটু উন্নত হয়ে। আসলে ক্যাটারপিলার থেকেই এসব– ধারণার উদ্ভব। যেদিক দিয়েই যাক না কেন, বন্ধুরতার সাথে মানিয়ে নিতে পারে পুরোপুরি। যানগুলোর কিছু অংশ খোয়া গেলেও চলতে পারবে।
বেঁটে হাতির মতো একটা বাস ইয়া বড় শুড় নিয়ে চান্দ্রযানের গায় সেঁটে যাচ্ছে, এ ঔড়ই শিপ থেকে বাসে ওঠার পথ। কয়েক সেকেন্ড পরেই বাইরে ধাতব শব্দ আর বাতাসের হিসহিসানি শোনা গেল। বাতাসের সংযোগ হবার সাথে-সাথেই এয়ার প্রেশার ঠিক হয়ে গেছে। এয়ারলকের ইনার ডোর খুলে যাবার পর স্বাগত জানানোর মেজবানরা প্রবেশ করল সম্মানিত মেহমানকে বেসে নিয়ে যেতে।
এগিয়ে ছিল র্যালফ হ্যাভোরসেন, সে সাউদার্ন প্রভিন্সের প্রশাসক-এর মানে হল, সে শুধু বেসের শাসনকর্তা নয়, বরং দক্ষিণ চাঁদের সব অভিযানের নিয়ন্তা। সাথে চিফ সায়েন্টিস্ট ডক্টর রয় মাইকেলস। এই ছোট্ট অবয়বের জিওফিজিসিস্টকে ফ্লয়েড আগের চন্দ্রভ্রমণগুলোর সময় থেকেই চিনত। আর আছে আধ ডজন সিনিয়র বিজ্ঞানী, প্রশাসক। তাকে সম্মানের সাথে তারা রিসিভ করল। কোনো এক গোপন গুরুভার যে তাদের উপর থেকে নেমে গেল ফ্লয়েড আসার পর সেটা তাদের দেখেই বোঝা যায়। নিজেদের দুঃখ কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে তারা যে উন্মুখ ছিল এতটা অন্তত স্পষ্ট।
‘আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত, ডক্টর ফ্লয়েড,’ অফিসিয়াল মনোভাব নিয়ে বলল হ্যাভোরসেন, ‘ট্রিপটা ভালো কেটেছে তো?’
‘চমৎকার,’ জবাবে ফ্লয়েড জানায়, এরচে ভাল হতেই পারে না। কুরাতো সারাক্ষণ যত্নআত্তি করেই কাটাল।
এরপর সেই পুরনো বিরক্তিধরানো শুভেচ্ছাবাণী বাকীদের সাথেও কপচিয়ে নিয়ে চড়তে হল বাসে। না বলা কোনো চুক্তির বলেই যেন তারা কেউ তার হঠাৎ এই ভিজিটের ব্যাপারে কোনো কথাই বলল না। হাজারখানেক ফুট পেরিয়ে বাস এলো একটা বড় লেখার সামনে
ক্যাভিয়াস বেসে স্বাগতম
ইউ এস অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর[২২]
১৯৯৪
ফ্লয়েড এবার দেখতে পায় লেখাটা দুভাগে বিভক্ত হয়ে মাটির তলার পথ দেখাচ্ছে। এক বিশাল দরজা খুলে গিয়ে তাদের বেসের পেটে প্রবেশাধিকার দেয়। তারপর যায় বন্ধ হয়ে। পরপর তিনটি দরজা পেরিয়ে তারা বাতাসের গর্জন শুনতে পেল। আবার এসেছে বায়ুমণ্ডল।
পাইপ আর ক্যাবলে ভর্তি এক টানেল ধরে পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে তারা এক্সিকিউটিভ এরিয়াতে হাজির হয়। চির পরিচিত অফিসিয়াল সেই টাইপরাইটার, অফিস কম্পিউটার, মহিলা এসিস্ট্যান্ট, ওয়ালচার্ট আর গোঙাতে থাকা টেলিফোন দেখে বেশ স্বস্তি বোধ হচ্ছে ডক্টর ফ্লয়েডের। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর লেখা দরজার সামনে আসতেই আবার ফিরে আসে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হ্যাভোরসেনের সেই অফিসিয়াল ভাব, ‘ডক্টর ফ্লয়েড আর আমি দু মিনিটের মধ্যেই ব্রিফিং রুমে হাজির হচ্ছি।’
বাকীদের কেউ নড করল, কেউবা সম্মতিসূচক শব্দ তুলে করিডোর ধরে নেমে গেল। কিন্তু হ্যাভোরসেন ফ্লয়েডকে নিজের অফিসে নিয়ে যাবার আগে ছোট্ট এক সমস্যায় পড়ে। দরজা খুলে যাবার সাথে-সাথেই এক খুদে অবয়ব ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্যাভোরসেনের উপর।
‘ড্যাডি!’ তুমি উপরে গিয়েছিলে! আমাকে নেয়ার প্রমিজ ছিল তোমার!
‘ডায়না, আমি বারবার বলেছি, সম্ভব হলে নিয়ে যাব। এখন ডক্টর ফ্লয়েডের সাথে খুব ব্যস্ত আছি-হ্যান্ডশেক করো। ইনি এইমাত্র পৃথিবী থেকে এলেন।’
ফ্লয়েডের মনে হল ছোট্ট মেয়েটার বয়স আটের মতো হবে। হাতগুলো সরু সরু। মেয়েটার চেহারা পরিচিত লাগছে খুব। এবং হঠাৎ করেই ফ্লয়েড বুঝতে পারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কেন মিটিমিটি হাসছে।
‘অবিশ্বাস্য! শেষ যেবার এখানে এলাম তখন ও-তে একদম ছোট ছিল!’
‘গত হপ্তায় ওর চতুর্থ জন্মদিন গেল। এই লো গ্র্যাভিটিতে বাচ্চাকাচ্চা দ্রুত বাড়ে। কিন্তু বয়সটা অত দ্রুত বাড়ে না। ওদের শরীরের কলকজা নষ্ট হবে না সহজে। বাঁচবে আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।’
বিভ্রান্ত লোকের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ফ্লয়েড, এ-মেয়েতো উচ্চতায় প্রায় লেডি হয়ে গেছে এরিমধ্যে! মনে হচ্ছে ওর হাড়ের গঠন খুবই ভালো।
‘নাইস টু মিট ইউ এগেইন, ডায়না,’ এরপরই-কোনো এক প্রবণতায়, কোনো এক কৌতূহলে এক যুগজিজ্ঞাসা বেরিয়ে পড়ে আপনাআপনি মুখ থেকে, পৃথিবীতে যেতে চাও তুমি?
চোখদুটো দ্যুতি ছড়ালো একটু, হাত ঝাঁকিয়ে নিল মেয়েটা।
‘সেটাতো বাজে জায়গা। পড়ে গিয়ে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ব্যথা দাও। আর তোমাদের চারিদিকে মানুষ ভর্তি।
এইতো, স্পেসবর্নদের ফার্স্ট জেনারেশন! নিজেকে শোনায় ফ্লয়েড। সামনের বছরে ওরাই বেড়ে চলবে। চিন্তার কোথায় যেন দুঃখের সাথে আশা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আজ আমাদের পৃথিবী কত্তো পুরনো, কত বেশি প্রকাশিত! এখানে নতুন পাবার কিস্যু নেই। কিন্তু অভিযাত্রীদের মৃত্যুশীতল অভিযানের অন্যদুয়ার খোলা, অভিযান চলবেই। আজ তাদের যন্ত্রপাতির মধ্যে কুঠার আর বন্দুক থাকবে না, তাদের যানবাহন হবে না ওয়াগন কিংবা ক্যানো। থাকবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, পরমাণুর শক্তি চালাবে সবকিছুকে, প্লাজমা ড্রাইভের শক্তি খুঁড়ে দেবে আকাশকে, ফার্মগুলো হয়ে পড়বে হাইড্রোপোনিক। আসছে এগিয়ে সময়টা, আর সব মায়ের মতো বসুমতাঁকেও তার সন্তানের প্রতি বিদায়বাণী উচ্চারণ করতে হবে উদাত্ত কণ্ঠে।
মেয়ের কাছে একগাদা নতুন প্রমিজ করে, বেশ বকাবকি করে হ্যাভোরসেন ফ্লয়েডের সাথে একা কথা বলার সুযোগ পেয়ে যায়। প্রশাসকের অফিস স্যুটটা বড়জোর পনের স্কয়ার ফুট। কিন্তু এ ছোট্ট ঘরে বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার ডলার পাওয়া অফিসারের মাননুযায়ী সব সরঞ্জামই বহাল তবিয়তে দাঁত কেলিয়ে হাসতে পারছে। বিশ্বের সব বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অটোগ্রাফসহ ছবি ঝুলছে দেয়ালে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বা জাতিসংঘের মহাসচিবও বাদ যাননি। অপর দেয়ালের দখলদার বিশ্বের তাবৎ বড় অ্যাস্ট্রোনটের ছবি। সেগুলোও স্বাক্ষরসহ।
এক তথাকথিত ‘লেদার’ সোফার ভিতর ডুবে গিয়ে একগ্লাস ‘শেরি’ হাতে পায় ফ্লয়েড। আতিথেয়তার এই পুরনো মদটি আসলে চান্দ্র জৈব-রসায়নবিদদের অবদান। প্রথমে একটু সাবধানে চুমুক দেয় সে, তারপর আরামে।
‘তা, চলছে কেমন, র্যালফ?’
‘খুব একটা খারাপ না,’ হ্যাভোরসেন জবাব দেয় চিন্তিতমুখে, বরং সেখানে যাবার আগে একটা ব্যাপার তোমার মাথায় থাকা ভালো।
‘কী?’
‘আসলে, আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে তুমি নৈতিক সমস্যা বলতে পার…’
দীর্ঘশ্বাস ফেলে দক্ষ প্রশাসক।
‘তাই!’
‘এখনো ব্যাপারটা সিরিয়াস নয়, কিন্তু হতে কতক্ষণ?’
সরল মনে বলে বসে ফ্লয়েড, ‘নিউজ ব্ল্যাকআউট? খবর দেয়া বন্ধ করেছ সেটা?’
‘হু। আমার লোকজন গরম হয়ে উঠছে এ ব্যাপারটা নিয়ে। হাজার হলেও, প্রায় সবাই পৃথিবীতে পরিবার ফেলে এসেছে। সেসব মানুষ প্রায় বিশ্বাস করে বসে আছে যে আমরা সবাই মুনপ্লেগের শিকার।’
‘আ’ম স্যরি অ্যাবাউট দ্যাট,’ বলল ফ্লয়েড, কিন্তু কোনো পত্রিকাই এরচে ভালো কভার স্টোরির আইডিয়া পায়নি। হাজার হলেও, গুজবটা কাজে লেগেছে। ও, ময়শেভিচের সাথে স্পেস স্টেশনে দেখা হয়েছিল। এমনকি সেও একই কথা বলছে।’
‘এতেই সিকিউরিটি সন্তুষ্ট হবে।’
‘খুব বেশি তুষ্ট হবার কিছু নেই, সে টি এম এ-১ এর কথাও বলেছে। কথাগুলো কোনো ফাঁকফোকড় ধরে যে বেরিয়ে পড়বে তার নেই ঠিক। এখন আমাদের কিছুই করার নেই। আগে জানতেই হবে, মরার জিনিসটা কী, তারপর জানতে হবে পেছনে চাইনিজ বন্ধুরা আছে কিনা, সবশেষে স্টেটমেন্ট। তার আগে সেটার অস্তিত্ব ঘোষণা করলে আমাদেরই বারোটা বাজার সম্ভাবনা।’
‘ডক্টর মাইকেলস মনে করে সে সঠিক জবাবটা জানে। তোমাকে বলার জন্য নিশ্চয়ই ওর পেট ফেটে যাচ্ছে।’
ফ্লয়েড নামিয়ে রাখে নিজের গ্লাসটা। ‘আর আমার মন ওর কথা শোনার কৌতূহলে ফেটে পড়ছে।’
অধ্যায় ১১. বিশৃঙ্খলা
মিটিং রুমটায় শত মানুষ সহজেই ধরে যাবে। এখানে আছে সর্বাধুনিক অপটিক্যাল আর ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লের ব্যবস্থা। দেখতে একেবারে আদর্শ কনফারেন্স রুমেরই মতো; এর সাথে পোস্টার, পিন পেপার আর নবীস আঁকিয়ের চিত্র দেখা যাচ্ছে দেয়ালজুড়ে। এর মানে জায়গাটা স্থানীয় সংস্কৃতিরও আজ্ঞা। ফ্লয়েড প্রায় ধাক্কা খেয়ে বসেছিল একটা ছবির কালেকশনের সাথে। সেখানেও ফটোগ্রাফারের স্বাক্ষর জ্বলজ্বল করছে। পৃথিবী থেকে এগুলো আনতেই সবচে কম কষ্ট আর খরচ হয়, বোঝা যায়। সবগুলোর নামই চমৎকার, দয়া করে ঘাস থেকে দূরে থাকুন… দিনের বেলায়ও পার্কিং নিষিদ্ধ… ডিফেন্স ডিফিউমার… সামনে সৈকত… গবাদিপশু পার হওয়ার পথ… নরোম কাঁধ আর পশুকে কোনো খাবার দেবেন না।
এত রুদ্র পরিবেশেও মানুষ তার ফেলে আসা ভুবন নিয়ে স্মৃতি রোমন্থনে মাতে, ঠাট্টা করে, কিন্তু তাদের পরের প্রজন্ম সেই দুনিয়া আর তার এসব ফালতু ব্যাপারকে মোটেও পাত্তা দেবে না।
ফ্লয়েডের আসার অপেক্ষায় বসে আছে জনাপঞ্চাশেক লোক। এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পেছন পেছন ঢোকার পর সবাই সম্মানের সাথে উঠে দাঁড়ায়।
পরিচিত কয়েকটা মুখের দিকে তাকিয়ে একটু নড় করেই ফ্লয়েড বলে ওঠে, ‘বিফ্রিংয়ের আগে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই।’
অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মঞ্চে উঠে গিয়ে উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করছে এমন সময় ফ্লয়েড সামনের সারিতে বসে পড়ল।
‘লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন,’ শুরু করে হ্যাভোরসেন, ‘আমার আবার বলে নেয়া উচিত, এ এক জরুরী মুহূর্ত। নিজেদের মধ্যে ডক্টর হেউড ফ্লয়েডকে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আমরা সবাই তাঁর কাজের দ্বারা পরিচিত, আমি ও কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেও তাকে চিনি। তিনি এইমাত্র পৃথিবী থেকে একটা স্পেশাল ফ্লাইটে এসেছেন। ব্রিফিংয়ের আগে আগে তাঁর কিছু কথা বলার আছে। ডক্টর ফ্লয়েড।’
ছোট্ট একটু হাসি দিয়ে এগিয়ে গেল ফ্লয়েড, ‘থ্যাঙ্ক ইউ, এটুকুই শুধু বলতে চাই আমি। প্রেসিডেন্ট আমাকে বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন যেন আপনাদের অসাধারণ কাজের জন্য শুভেচ্ছাবাণী পৌঁছে দিই। আশা রাখি আমরা কী পেয়েছি তা অতি শীঘ্ন বুঝতে পারব। আমি একটা ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন যে, এখানটায় একটু স্পষ্ট করে কথাগুলো বেরিয়ে আসে মুখ থেকে, আপনাদের কেউ কেউ কিংবা সবাই চান রহস্য আর গোপনীয়তার চোর পুলিশ খেলাটা তুলে দিতে। আসলে এটা না ভাবলে আপনাদের পক্ষে বিজ্ঞানী হওয়া সম্ভব হতো না।’
চোখ পড়ল ডক্টর মাইকেলসের উপর। নিজের গালে বিশাল একটা ক্ষত-চিহ্ন দিয়ে মাথা উঁচু করে মনোযোগের সাথে ফ্লয়েডের কথা শুনছে বিজ্ঞানী। বোঝাই যায় স্পেসে কোনো দুর্ঘটনা হয়েছিল বেচারার। শক্ত চোখমুখের কারণে আরো বোঝ যায় যে সে ফ্লয়েডের পরের বাক্যে, ‘চোর-পুলিশ খেলা’ কথাটা পছন্দ করেনি।
‘কিন্তু আমার বলা উচিত, যে, এ এক বিশেষ পরিস্থিতি। আমাদের নিজেদেরকে আগে এ নিয়ে নিশ্চিত হতে হবে। একবার, মাত্র একবার যদি ভুল করে বসি, তাহলে কোনো দ্বিতীয় সুযোগ মিলতে নাও পারে, তাই কষ্ট করে আর একটু ধৈর্য ধরুন। প্রেসিডেন্টেরও একই অভিমত।
‘এটুকুই আমার বলার ছিল। এবার আপনারা রিপোর্ট পেশ করতে পারেন।’
নিজের সিটে ফিরে গেলে প্রশাসক বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, ডক্টর ফ্লয়েড।’ আর তারপরই তার সিনিয়র বিজ্ঞানবিদদের দিকে ঘাড় কাৎ করল। সাথে সাথে উঠে এল মাইকেলস। এবার চারদিকের আলো একটু ফিকে হয়ে আসে। এতে করে শ্ৰোতাকুলের মনোযোগ বক্তার দিকে আকৃষ্ট হবে।
চাঁদের একটা ছবি স্ক্রিনের উপর ভেসে উঠতেই দক্ষিণ-মধ্য চাঁদের এক জ্বালামুখের দিকে সবার দৃষ্টি যায়। তীব্র এক আলো উঠে এসেছে সেখান থেকে। যেন কেউ চাঁদের মুখে একগুচ্ছ ফুল গুঁজে দিয়েছে, আর সেটা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।
‘এ হল টাইকো,’ বলছে মাইকেলস, একে বরাবর উপর থেকে দেখলে এত অস্পষ্ট দেখা যায় যতটা পৃথিবী থেকেও দেখা না যায়। কিন্তু এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখেন তো আপনারা বুঝতে পারবেন কী করে চাঁদের এই জ্বালামুখটা গোলার্ধ দখল করে রেখেছে।
সে ফ্লয়েডকে এই অতি পরিচিত জিনিসের অতি অপরিচিত চিত্র হজম করার মতো সময় দিয়ে বলতে লাগল, গত বছর থেকে এ এলাকায় আমরা একটা ম্যাগনেটিক সার্ভে করছি। চৌম্বকীয় নিরীক্ষণটা চালানো হয় নিচু স্যাটেলাইট থেকে। সার্ভে শেষ হয় মাত্র গতমাসে আর এ হল তার ফল-এই ম্যাপটাই পুরো সমস্যার সূত্রপাত করে।
আরেক ছবি ভেসে উঠল যেটা শুধু বস্তুর ত্রিমাত্রিকতা দেখায়, আউটলাইন দেখায়। ম্যাপটায় দেখা যাচ্ছে চৌম্বকীয় অবস্থা। বেশিরভাগ স্থানেই রেখাগুলো সমান্তরাল আর সমান। কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে সেসব রেখা জট পাকিয়ে যায়। যেন একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে শৈল্পিক বৃত্ত বানানো হয়েছে।
একেবারে গোবেচারা চোখেও এটুকু ধরা পড়বে যে, চাঁদের এ অংশের চৌম্বকক্ষেত্রে কোনো একটা গণ্ডগোল চলছে। সেই মানচিত্রের একেবারে নিচে বড় অক্ষরে লেখা: টাইকো চৌম্বকীয় বিশৃঙ্খলা–এক (টি এম এ-১)। এর একেবারে কোণায় স্পষ্ট করে লিখে দেয়া আছে, ‘অত্যন্ত গোপনীয়।
‘প্রথমে আমরা ধরে নিলাম এটা কোনো বহির্জাগতিক শিলার কাণ্ড। কিন্তু সব তথ্যপ্রমাণ এর বিপরীতে যাচ্ছে। অগত্যা একটু চোখ বুলাতেই হলো।’
‘প্রথম দল কিস্য আবিষ্কার করতে পারেনি। এটুকু বুঝতে পেরেছে যে, স্বাভাবিক লেভেলটা চাঁদের মাটির একটু ভিতরের দিকে দেবে যায়। ওরা একটা ড্রিল দিয়ে ঠিক মধ্যখানে খোঁড়া শুরু করেছিল স্যাম্পলের আশায়। বিশ ফুট নিচে ড্রিলটা থেমে গেল। তারপরই সার্ভে পার্টি খননকাজ শুরু করে, স্পেসস্যুটের ভিতরে থেকে কাজটা বেশি সুবিধার না, আপনাদের এটুকু বলতে পারি।
‘যা পেল তা নিয়েই তড়িঘড়ি করে ফিরে এল বেসে। ভালো ইকুপমেন্টসহ একটা বড় দল পাঠালাম এবার। এবারের যুদ্ধ চলল দু হপ্তা ধরে। ফলাফল আপনারা জানেন।’
স্ক্রিনের ছবি বদলের সাথে সাথে অন্ধকার কনফারেন্স রুমের পরিবেশও বদলে গেল। প্রত্যেকেই বহুবার দেখেছে দৃশ্যটা, তবু নতুন কিছু পাবার আশায় সবার চোখ স্থির হয়ে রইল ছবির উপর। গোটা পৃথিবী আর চাঁদের মধ্যে একশোজনও এ ছবির উপর চোখ ফেলার অনুমতি পায়নি।
উজ্জ্বল লাল আর হলুদ স্পেসস্যুট পরা এক অভিযানকারী কোনো এক খননকৃত এলাকায় দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা অবশ্যই রাতের। চাঁদ বা মঙ্গলের যে কোনো স্থানে এমন দৃশ্য দেখা যেতে পারে। কিন্তু তারপরও কোনো গ্রহে কোনোদিন এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা হয়নি।
যে বস্তুর সামনে স্যুট পরা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা এক মিষমিষে কালো স্ল্যাব। উচ্চতায় মোটামুটি দশফুট আর প্রস্থে পাঁচ। এক পলক দেখেই সুবিশাল কবরফলকের কথা মনে পড়ে যায় ফ্লয়েডের। একেবারে নিখুঁত পালিশ করা। মনে হয় সবটুকু আলো শুষে নিচ্ছে। কোনো খুঁত নেই উপরিতলের। কী দিয়ে তৈরি তা বলারও যো নেই। হতে পারে পাথর, প্লাস্টিক, অথবা ধাতু…অথবা মানুষের অজানা কোনো উপাদানও হতে পারে।
‘টি এম এ-১,’ ডক্টর মাইকেলস দরাজ গলায় ঘোষণা করে, ‘এটাকে দেখে ব্র্যান্ড নিউ মনে হয়, তাই না? আসলে তাদের খুব একটা দোষ দেয়া যায় না যারা বলবে এ জিনিস বড়জোর বছর কয়েকের পুরনো। কেউ আবার এটাকে আটানব্বইয়ের তৃতীয় চৈনিক অভিযানের সাথে গুলিয়ে ফেলার পাঁয়তারা ভাজছে। কিন্তু আমি কশিনকালেও সেসব কথায় কান দিইনি-আর এবার আমরা এর বয়স নিয়ে একটু মাতামাতি করতে পারি। তথ্যসূত্র? স্থানীয় ভূতাত্ত্বিক প্রমাণগুলো।
‘ডক্টর ফ্লয়েড, আমার কলিগরা আর আমি আমাদের সারা জীবনের সব সুনাম এর উপর বাজী লাগাতে রাজী। টি এম এ-১ এর সাথে চাইনিজদের কোনোকালে কোনো সম্বন্ধ ছিল না। বলতে গেলে, এর সাথে মানবজাতির আদৌ কোনো সম্বন্ধ নেই। কারণ, যখন এটাকে কবর দেয়া হয় তখন মানুষ বলতে কিছু ছিল না।
‘দেখতেই পাচ্ছেন, এটা তিন মিলিয়ন বছরের পুরনো। ত্রিশ লাখ সাল পেরিয়ে গেছে। এখন, দ্রমহোদয়গণ, আপনারা যেটার দিকে তাকিয়ে আছেন তা হল পৃথিবীর বাইরে বুদ্ধিমত্তার প্রথম প্রমাণ।’
অধ্যায় ১২. ধরণী-জোছনায় যাত্রী
ম্যাক্রো ক্র্যাটার প্রভিন্স: এস এর মতো একটা অংশ বেরিয়ে আছে সবচে সামনের জ্বালামুখ থেকে। চাঁদের দৃশ্যমান অংশে অবস্থিত। ই এর মতো বেরিয়ে থাকে সেন্ট্রাল ক্র্যাটার প্রভিন্স থেকে। এখানে-সেখানে হাজারো জ্বালামুখ। এখানেই চাঁদের সবচে বড়টা সহ অনেক বড় বড় অগ্নিগিরিমুখ রয়েছে। এন এর মতো দেখতে অংশটায় কিছু প্রভাবশালী জিনিসপত্র চোখে পড়ে। বেশিরভাগ মুখই একটু খাড়া। কোনো কোনোটা দশ ডিগ্রি থেকে বারো ডিগ্রি। কোনো কোনোটার তলদেশ একেবারে সমতল।
নামা ও নড়াচড়া এবড়োথেবড়ো ভূমির কারণে ল্যান্ড করাটা কষ্টকর হবে। বরং সমতল জ্বালামুখের কোনোটায় নামলে সবচে বেশি সুবিধা হতে পারে। যে কোনো ধরনের মুভমেন্ট সহজ হবে, কিন্তু আগে থেকেই পথ নির্দিষ্ট করে রাখা দরকার। এক্ষেত্রেও সমতল জ্বালামুখের তলদেশে নড়াচড়া সুবিধাজনক।
গঠন: এখানে গঠন করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ প্রচুর আলগা পাথর ও পাথরের চাই পড়ে থাকে। এক্ষেত্রেও সমতল জ্বালামুখের তলদেশ সুবিধাজনক।
টাইকো: পোস্ট-মারিয়া জ্বালামুখ। ব্যাসে চুয়ান্ন মিটার। পরিধি সাত হাজার ন’ শ ফুট, তলা বারো হাজার ফুট নিচে। চাঁদের মধ্যে টাইকো রে সিস্টেম সবচেয়ে ভাল। এ থেকে পাঁচশো মাইলেরও বেশি দূরে আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দেয়া যায়।
(চাঁদের উপরিতলে বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং সমীক্ষা’ অফিস, চিফ অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য আর্মি-ইউ এস, ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ওয়াশিংটন, উনিশশো একষট্টি-থেকে নেয়া।)
এখন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল এলাকা চষে ফেলছে মোবাইল ল্যাব। জ্বালামুখের দিকে তোলাপাড় করে এগুচ্ছে আট চাকার বিশালদেহী ল্যাবরেটরিটা। দেখতে ছোটখাট একটা বেসের মতো। এর ভিতর বিশজন মানুষ হপ্তার পর হপ্তা আয়েশে কাটিয়ে দিতে পারে। বলা যায়, এ হল এক ভূমিতে চলা পরিপূর্ণ স্পেসশিপ। প্রয়োজনে উড়তেও জানে এ বিশেষ যানটি। কারণ নিচে আছে শক্তিশালী চারটি আন্ডারজেট।
বাইরে তাকিয়েই ফ্লয়েড দেখতে পায় সার ধরে পড়ে আছে কত ঝকমারি যানবাহন। প্রতিটিতেই একটা করে ফ্ল্যাশলাইট আছে, আছে ট্রেইল, সেই পথেও ফ্ল্যাশলাইট বসানো। দূরত্বটা দু’শ কিলোমিটার হলেও এই রাতে কেউ ক্ল্যাভিয়াস বেস থেকে টি এম এ-১ এর পথে যেতে চায় তাহলে হারিয়ে যাবে না।
মাথার উপরকার তারার দল একটু উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। নিউ মেক্সিকো বা কলোরাডোর ঝকঝকে আকাশ থেকেও নক্ষত্রলোক এত সুন্দর দেখা যাবে না। কিন্তু ঐ কয়লাকালো আকাশে এমন দুটি জিনিস আছে যা পৃথিবী-পৃথিবী ভাবকে পুরোপুরি উবিয়ে দেয়।
প্রথমটি ধরিত্রী স্বয়ং-উত্তর প্রান্তে আলোকবর্ষী এক গোলক সে। পূর্ণ চন্দ্র যত আলো বর্ষাতে পারে তারচে অর্ধশতগুণ আলো ঝরাচ্ছে আধ-পৃথিবী। পুরো ভূমিই যেন কিম্ভুত নীলচে সবুজ আলোর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত।
দ্বিতীয়টি হচ্ছে পুব আকাশে কৌণিকভাবে জ্বলতে থাকা ক্ষীণ আলোকমালা। এটা আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসছে। এই হল সেই অদ্ভুতুড়ে মহিমা যা কোনো মানুষ পৃথিবীতে বসে দেখার কথা কল্পনাও করতে পারে না। এই হলো করোনা, চান্দ্র সূর্যোদয়ের পূর্বসূরী। এ বহুক্ষণ ধরে বলে যায় যে মহান সূর্য একটু পরে চন্দ্রদেবের ঘুম ভাঙাবেন।
যাত্রীদের অবজার্ভেশন লাউঞ্জটা পাইলটের সিটের ঠিক পেছনে। হ্যাভোরসেন আর মাইকেলসের সাথে অবজার্ভেশন লাউঞ্জে বসেই সে দেখল তার ভাবনার জগৎ বারবার দোল খেয়ে যাচ্ছে। তিন মিলিয়ন বছরের পুরনো উপসাগরটা এই মাত্র তার সামনে নিজের পুরো বিস্তৃতি নিয়ে হাজির হল। আর সব অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর মতো ফ্লয়েডের চিন্তাও ঘুরেফেরে আরো বেশি বছরের আশপাশে। ত্রিশ লাখ বছর ইউনিভার্সের তুলনায় কিছুই নয়। তবু সেসময়ে কিছু তৈরি হয়নি। মন না, ভাবনা না, তৈরি হয়নি কোনো পরিণত মস্তিষ্ক।
ত্রিশ লাখ বছর! অসীম যেন তার বিস্তৃত ছবিকে তুলে আনল সামনে। লিখিত ইতিহাস, ইতিহাস কাঁপানো সেসব যুদ্ধবাজ নৃপতি, বিশ্বের প্রগতি আনন্দ-বেদনা, এই বিশাল সময় সাগরের হাজার ভাগের একভাগকেও ভরিয়ে তুলতে পারছে না। মানুষতে মানুষই, আজকের পৃথিবীর বেশিরভাগ প্রাণীই সেদিন ছিল না যেদিন চাঁদের বুকে বড্ড যত্ন করে এই কালো কিংবদন্তীকে কবর দেয়া হয়। কবর দেয়ার জায়গাটাও খুব হিসেব করে বের করা, চাঁদের সবচে উজ্জ্বল আর সবচে অদ্ভুত জ্বালামুখ!
এটাকে যে পুঁতে দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে ডক্টর মাইকেলস একেবারে নিশ্চিত।
‘প্রথমে,’ মাইকেলস ব্যাখ্যা করে, ‘আমি ধরে নিই যে এটা কোনো লুকায়িত জিনিস নির্দেশ করছে। কিন্তু আমাদের সর্বশেষ অভিযানে এর উল্টো ফল বেরোয়। জিনিসটা বসে আছে একই বস্তুতে তৈরি প্ল্যাটফর্মের উপর। তার নিচে নিরেট পাথর। এর… স্রষ্টারা… জানত যে একে টিকে থাকতে হবে চাঁদের সব ভূকম্পন সয়ে গিয়ে। তারা জিনিসটাকে বসিয়েছিল অসীম সময়ের জন্য।’
মাইকেলস এখনো হতাশা আর আশার মিশ্রিত সুরে বলে যায়, ফ্লয়েড দু অনুভূতিকেই প্রবাহিত করে নিজের ভিতর। শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রাচীনতম প্রশ্নের মধ্যে একটার জবাব মিলেছে। এই একমাত্র সভ্যতা নয়; ইউনিভার্স আরো বুদ্ধিমত্তার জন্মদাতা। একই সাথে সময়ের ব্যাপারটা ভাবিয়ে তোলে সবাইকে। যাই এখান দিয়ে গিয়ে থাক না কেন, সেটা মানব সভ্যতাকে হাজায়ো প্রজন্মের ব্যবধানে না দেখেই চলে গেছে। আর আমরা তাদের সম্পর্কে আজ হঠাৎ করে কীই বা জানব, যারা আকাশ ভেদ করে চলে গেছে সেই যুগে যে যুগ আমাদের পূর্ব পুরুষদের বাস করাতো গাছের ডালে ডালে।
চাঁদের অতি ছোট দিগন্তের কাছাকাছি একটা সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। ঝকঝকে সিলভার ফয়েলে মোড়া একটা তাঁবুর মতো জিনিস সেদিকে। অবশ্যই সেই ফয়েলটা দিনের অসভ্য আলোর বিরুদ্ধে কাজে দেয়। বাস চলা শুরু করলে ফ্লয়েড শক্তিশালী দিনের আলোয় পড়তে পারে:
ইমার্জেন্সি ডিপো নং-৩
বিশ কিলো লক্স[২৩]
দশ কিলো পানি
বিশ ফুডপ্যাক এম কে ফোর
এক টুলকিট (টাইপ বি)
এক সট রিপেয়ার আউটফিট
টেলিফোন!
‘এ নিয়ে ভেবেছিলে কিছু?’ প্রশ্ন করে ফ্লয়েড, জানালার বাইরে তার হাত নির্দেশিত, ‘ধরো জিনিসটার সাপ্লাই ফুরিয়ে গেল, তখন?’
‘এমন সম্ভাবনা আছে,’ স্বীকার করে মাইকেলস, ‘সেই ম্যাগনেটিক ফোর্সটি হঠাৎ করেই আবার ঠিক হয়ে যায়। ফলে গোলযোগের সামান্য এলাকাটা পাওয়া কোনো নাভিশ্বাস তোলার মতো কষ্টের ব্যাপার না। আর ম্যাগনেটিক বিশৃঙ্খলার এলাকাটা নিতান্তই ঘোঁট। বেশি সাপ্লাইয়ের দরকার পড়ে না।’
নাক গলায় হ্যাভোরসেন, কেন নয়? কে জানে তারা কত বড় ছিল? হয়তো তারা ছিল ছয়ইঞ্চির লিলিপুট, এটা তাদের কাছে ত্রিশতলার বিল্ডিংয়ের সমান হবে।
মাইকেলস উত্তেজনায় নিজের হাত নাড়ে, ‘আউট অব কোশ্চেন। বুদ্ধিমান প্রাণীর জন্য ন্যনতম একটা মস্তিষ্ক আকুতি প্রয়োজন।’
মাইকেলস, হ্যাভোরসেন আর ফ্লয়েড-তিনজনেই বলে যায় নিজের নিজের কথা, গুরুত্ব দিয়ে শোনে অন্যের মতামত। কিন্তু একটু ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বও যেন ধরা দিচ্ছে তাদের কথায়।
একটা ব্যাপারে তাদের মতভেদ নেই, তা হল টি এম এ-১ বা টাইকো মনোলিথ। সব রহস্য এর ভিতর লুকিয়ে আছে। চাঁদে নামার পর গত ছ’ঘণ্টায় ফ্লয়েড অন্তত বারোটা থিওরী শুনেছে। কিন্তু তার নিজের কোনো তত্ত্ব নেই। ধর্মমন্দির, প্রাচীন সমাধি, রত্নভাণ্ডার, সার্ভে মার্কার, জিওফিজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট-আরো কত কী! কোনো কোনো মৌলবাদী’ একরোখা বিজ্ঞানীর কথাবার্তা আরো ভয়াল। অনেক বাজী ধরা হয়েছে এরি মধ্যে, আর সত্যিটা বেরিয়ে পড়লে হাতবদল হবে বেশ বড়মাপের কারেন্সি। অবশ্য একটা কথা থেকে যায়, আদৌ সত্য উদ্ঘাটন হবে তো!
একটু স্যাম্পল তুলে আনার জন্য মাইকেলস আর তার সঙ্গীসাথীদের করা সব ভদ্ৰ চেষ্টাকেই বিফল করে দিয়েছে সেই অভদ্র কালো স্তম্ভটা। তাদের কোনো সন্দেহই নেই যে একটা লেজার বিম চালালে সহজেই জিনিসটাকে কাটা যায়, কিন্তু বাস্তবে কিছুই ঐ ভয় ধরানো জিনিসের গা থেকে একটা চুল সরিয়ে আনতে পারেনি। এবার লেজার চালানোর মতো বড় সিদ্ধান্ত নির্ভর করে ফ্লয়েডের উপর।
এক্স রে, সনিক প্রোব[২৪], নিউট্রন বীম[২৫] এবং আর সব নিরাপদ পদ্ধতি আগে চেখে দেখা হবে। লেজারের ভারি গোলাবারুদ যুদ্ধক্ষেত্রে নামানো হবে তার পর। এ হল বর্বরের কাজ। তুমি কোনো জিনিসকে চিনতে পারছ না, সমস্যা কোথায়, ভেঙে দেখ! কিন্তু মানুষ সম্ভবত বর্বর জাতির সদস্য, গত শতাব্দীগুলোয় তারা সব সময় এ পথই অনুসরণ করেছে।
আর কোত্থেকে তারা এসে থাকতে পারে? স্বয়ং চাঁদের বুকে? না, এ একেবারে অসম্ভব। যদি এর বুকে একটাও প্রাণী থাকত তাও গত জ্বালামুখ-গঠন যুগে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা। তখন চান্দ্র-উপরিতলের বেশিরভাগই ছিল আগুন-তপ্ত।
পৃথিবী থেকে সেই সভ্যতার শুরু নয়তো? খুবই বেখাপ্পা। কিন্তু হতেওতো পারে। কোনো অতি অগ্রসর পার্থিব প্রাণী-হয়তো তারা মানুষ নয়-প্লেইস্টোসিন এরার নিষ্ঠুর দিনগুলোতে…নাহ্! আরো হাজার প্রমাণ তারা রেখে যেত পৃথিবীর বুকে। চাঁদে আসার বহুদিন আগে থেকেই আমরা সে বিষয়ে সব জেনে ফেলতাম, ভাবে ফ্লয়েড।
আর মাত্র দুটি বিকল্প সামনে-গ্রহকুল আর নক্ষত্রলোক। এরি মধ্যে সৌর জগতের আর কোথাও সভ্যতার ছিটেফোঁটা থাকার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়া হয়েছে। এমনকি কোনো ধরনের জীবন থাকার সম্ভাবনাও নেই পৃথিবী আর মঙ্গল ছাড়া। ভিতরের গ্রহগুলো একদম গরম আর বাইরেরগুলো বরফশীতল। কোনো কোনোটার ভূমিতে আবার প্রতি স্কয়ার ইঞ্চিতে বায়ুচাপ শত শত টন, সেখানে জীবন গড়া অসম্ভব।
সুতরাং, এই পরিদর্শকদল হয়তো এসেছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি থেকে। এবার এটাতো আরো অসম্ভব মনে হচ্ছে। চাঁদের নগ্ন আকাশের দিকে খোলা চোখে সে তাকায়। কিছু একটা খোঁজে। তার মনে আছে কীভাবে মাঝেমধ্যেই তার বন্ধু বিজ্ঞানীরা ‘প্রমাণ’ দেখিয়েছে যে আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণ অসম্ভব। আজো পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে যাত্রাটা দেখতে শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু সবচে কাছের তারকা হাজার লাখ গুণ দূরত্বে ঘুরপাক খাচ্ছে… আকাশকুসুম ভাবনাচিন্তায় ডুবে থাকা এখন সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আরো প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
‘দয়া করে আপনার সিটবেল্ট বেঁধে নিন এবং সব আলগা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন,’ হঠাৎ করেই কেবিন স্পিকার বলে উঠল, ‘সামনে চল্লিশ ডিগ্রি অবনমন।’
একেবারে দূরপ্রান্তে দুটি মার্কারপোস্ট দেখা যাচ্ছে। ফ্লয়েড কোনোমতে নিজেকে সামলে নিতেই বাসটা প্রবেশ করে খাড়া খাঁজের ভিতর। যেন কোনো ঘরের ঢালু ছাদ বেয়ে নেমে চলছে অনেকক্ষণ ধরে। এখন আর পৃথিবীর মিনমিনে আলো তেমন দেখা যাচ্ছে না। কারণ এই ঢাল। বাসের নিজস্ব ফ্লাডলাইট জ্বালতে হল। বহুবছর আগে ফ্লয়েড ভিসুভিয়াসের ঠোঁটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। একেবারে জ্বালামুখের ভিতর। আজো সেই মুহূর্তের কথা মনে পড়ে গেল। তবে অনুভূতিটা খুব ঝেশ সুখদায়ক নয়।
ওরা টাইকোর ভিতরের কোনো এক সমভূমিতে নেমে যাচ্ছে। আরো কয়েক হাজার ফুট নিচে নেমে খাজ আবার উঠতে শুরু করবে। সামনের দিকে ঝুঁকে থেকে মাইকেলস মহোৎসাহে সমভূমি দেখাচ্ছে।
‘এইতো, সামনে।’ যেন নতুন কোনো বিস্ময়ের কথা শোনাচ্ছে সে। মাথা ঝাঁকায় ফ্লয়েড, কয়েক মাইল দূরের সবুজ আর লাল বাতিগুলো তার চোখে পড়েছে আরো আগেই। যদিও এই দানো-যানটা ভালোভাবেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছিল, তবু স্বভাব অনুযায়ী ফ্লয়েড সমভূমিতে নেমে যাবার আগ পর্যন্ত স্বস্তিতে শ্বাস নিতে পারেনি।
এবার পৃথিবীর আলোয় রূপালী বুদবুদের মতো চকচক করতে থাকা দুটি প্রেশার ডোম তার চোখে পড়ে। সাইটে কাজ করার মানুষের জন্য এগুলো তাঁবুর কাজে দেয়। কাছাকাছিই একটা রেডিও টাওয়ার, একটা ড্রিলিং রিগ, প্যাকেট করা বেশ কয়েকটা যানবাহন, আর বেশ বড় একটা খণ্ড পাথরের স্তূপ। একাকিত্বের মাঝে এই ছোট্ট ক্যাম্পটা দেখে বেশ দুঃখী মনে হয়। চারপাশে প্রকৃতির জমকালো নিষ্ঠুরতা। সেখানে নেই জীবনের কোনো চিহ্ন। বাইরে থেকে দেখে কেন যে মানুষ এখানে এসেছে তা বোঝাই যাবে না।
মাইকেলস বলছে, ‘যদি পাহাড়ের উপর যাও, ঐ রেডিও অ্যান্টেনার দিকে শ’খানেক গজ গেলে শুধু জ্বালামুখই দেখতে পাবে।’
তো, এই হল সেই আতঙ্ক! ভাবল ফ্লয়েড। এখন বাসটা প্রেশার ঢোমকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। সামনেই জ্বালামুখের ঠোঁট। একটু ভালোভাবে দেখার জন্য সে এগিয়ে গেল সামনে, সাথে সাথেই বেড়ে যাচ্ছে হৃদস্পন্দন। এখন বাহনটা এক বিশাল আধভাঙা পাথরে ওঠার পাঁয়তাড়া করছে। পাথরটা অগ্নিজ্বালামুখের ভিতরে। এবং সাথে সাথেই ঠিক সেসব ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল টি এম এ-১।
ফ্লয়েড একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, মিটমিট করে চোখদুটো, একটু নাড়ে নিজের মাথা, আবার তাকায় অপলক নেত্রে। এই তীব্র ধরণী জোছনাতেও জিনিসটাকে দেখা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রথমে মনে হয় যেন কার্বন পেপার থেকে কেটে তোলা এক সমতল চতুষ্কোণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যেন এর কোনো ঘনতুই নেই। অবশ্যই, এ এক দৃষ্টি বিভ্রম। এটা কঠিন বস্তু হলেও এর আলোক-প্রতিফলন এতই কম যে জিনিসটাকে না দেখে বরং এর আশপাশের আলোয় ভেসে যাওয়া এলাকা দেখে এর উপস্থিতি বুঝতে হচ্ছে।
জ্বালামুখে প্রবেশের সাথে সাথে সব যাত্রী একদম নিশুপ হয়ে গেল। আনন্দ আছে, আছে নিখাদ বিস্ময়, চাঁদ-মৃত চাঁদ তার বুকে এতবড় বিস্ময় লুকিয়ে রেখেছিল যুগ-যুগান্ত ধরে!
কালো স্ল্যাবের বিশ ফুটের মধ্যে এসেই বাস থেমে গেল। জিনিসটার আকৃতি একেবারে নিখুঁত জ্যামিতিক, সেটাতো জানা তথ্য, আরো কিছু দেখার বাকী রয়ে গেছে। এর অপ্রতিরোধ্য মসৃণ দেহের কোথাও কোনোরকম প্রতীক নেই, নেই চিহ্ন, কোনো প্রমাণ-কিছু নেই। এ যেন রাতের কঠিনীকৃত রূপ। আরো একটা তত্ত্ব কপচানোর চেষ্টা করে ফ্লয়েড, এটা চাঁদের জন্মের সময় গঠিত কোনো বিশেষ অস্বাভাবিক প্রাকৃতিকতার ফল নয়তো! তাইবা কী করে হয়, প্রকৃতি এমন নিখুঁত জ্যামিতিক হার হিসাব করবে কোনো দুঃখে? সবচে বড় কথা, এসব সম্ভাবনা আগেই ভেবে বাতিল করা হয়েছে।
জ্বালামুখের চারধারের ফ্লাডলাইটগুলো জ্বলে উঠতেই পরিবেশ পাটে গেল। চান্দ্র বায়ুশূন্য পরিবেশে আলোর কোনো রেখা দেখা যায় না। যদি বাতাস থাকত, ধূলিকণা যত্রতত্র ভেসে বেড়াতে পারত তাহলে অন্য কথা। চান্দ্র বায়ুমণ্ডল না থাকায় আলোর রেখাটা দেখা যায় না, শুধু দেখা যায় আলোর পতন।
আলোতে ভেসে গেছে চারদিক। দুধসাদা আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সবার। সেই কালো গায়ে এবারো আলো পড়েছে, কিন্তু ফল সেই একই। যেন সবটুকু আলো শুষে নিচ্ছে অপার আগ্রহে।
প্যানডোরার বাক্স[২৬] নাকি এটা? ভাবে ফয়েড। চির আগ্রহী মানুষের মতোই সে ভিতরটা দেখতে চায়, কিন্তু কী লুকিয়ে আছে এর ভেতর? কে জানে?
অধ্যায় ১৩. ধীর সূর্যোদয়
টি এম এ-১ সাইটের মূল প্রেশার ডোম এপাশ-সেপাশে মাত্র বিশ ফুট হলেও লোকে লোকারণ্য। ভিতরটায় একদম গাদাগাদি করে বিজ্ঞানীরা বসবাস করে। দুটি এয়ারলক আছে এ ডোমে। প্রথমটির সাথে যুক্ত একটা বাস। বাসটা দারুণ কাজে লাগছে। সেটাই এক স্বর্গীয় শোবার ঘর এখন। অন্য এয়ারলক দিয়ে বাকীরা যাতায়াত করে।
গোলার্ধের মতো দেখতে এ প্রেশারডোম-বুদ্বুদগুলো। দেয়াল থাকে দুটি। ভিতরের ছয় বিজ্ঞানী প্রত্যক্ষভাবে প্রজেক্টের সাথে জড়িত। বুদ্বুদের ভিতরেই তাদের বেশিরভাগ যন্ত্রকে স্থান দিতে হয়েছে। রান্নাবান্না, ধোয়ামোছা বা টয়লেটের আসবাবপত্রও ডোমের বিশাল অংশ জুড়ে থাকে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো তাদের সাথে ঘুমাতে দিতে হয় জিওলজিক্যাল সার্ভের সব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রকে, যেগুলোর ভ্যাকুয়ামে নষ্ট হবার সম্ভাবনা প্রকট। সব সময় এখান থেকেই চোখ রাখা যায় টি এম এ-১ এর উপর। তবু, ভিতরে ছোট টিভি স্ক্রিন রাখতেই হয়েছে।
হ্যাভোরসেন ডোমের ভিতর থাকার সিদ্ধান্ত নিলে ফ্লয়েড একটুও অবাক হয়নি। সে নিতান্ত ভদ্রভাবেই নিজের কথা জানায়।
‘আমি স্পেসস্যুটকে একটা প্রয়োজনীয় শয়তান মনে করি।’ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাফ-সুতরো নিজের কথা জানিয়ে দেয়, ‘বছরে চারবার এই গন্ধমাদন পর্বত নিজের ঘাড়ে চাপাই। প্রতিবারই চেক-আউটে খোলা চাঁদে বেরুতে হয় আমাকে। ব্যস। তোমরা কিছু মনে না করলে আমি এখানে থেকেই টিভিতে সব দেখব।’
আজো কয়েকটা কুসংস্কারকে টেনে তোলা যায়নি। এখন আর স্পেসস্যুট কোনো গন্ধমাদন পর্বত নয়। কিন্তু সেসব বিজ্ঞানীর কেউ ব্যাপারটাকে বুঝতে পারবে না। প্রথম চান্দ্র অভিযানে যে জবরজঙ স্পেসস্যুট পরতে হয়েছিল তার তুলনায় আজকেরটা নস্যি। এগুলো গায়ে চাপাতে এক মিনিটও লাগে না। প্রয়োজন পড়ে না কারো সাহায্যের, এমনকি কোনো স্যুটতো অটোম্যাটিক। যে এম কে ফোরের ভিতর ফ্লয়েড নিজেকে এইমাত্র সিলগালা করে নিল সেটা চাঁদের চরম বৈরী পরিবেশ থেকেও তাকে বাঁচাবে নির্দ্বিধায়।
ডক্টর মাইকেলসের সাথে সে ঢুকে পড়ল এয়ারলকের ভিতরে। এবার, ছোট্ট বেসের শব্দ মিলিয়ে যেতেই নিজেকে সে আবিষ্কার করে চান্দ্র-শূন্যতার এক অসীম জগতে।
এই নীরবতায় চিড় ধরেছে তার স্যুট রেডিওর নাক-গলানো কথাবার্তায়।
‘প্রেশার ঠিক আছে তো, ডক্টর ফ্লয়েড? শ্বাস নিতে পারছেন ঠিকমতো?’
‘হ্যাঁ-একেবারে ঠিকমতো চলছে সবকিছু।’
অন্যদিকে মাইকেলস বাইরে থেকে সবকিছু দেখে নিয়ে বলে উঠল, ‘এবার যাওয়া যাক।’
আউটার ডোরটা খুলে যেতেই রুক্ষ প্রান্তর পৃথিবীর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সামনে খোলা পথ।
লকের ভিতর দিয়ে বেশ কসরৎ করে ফ্লয়েড অনুসরণ করে মাইকেলসকে। কিন্তু আদৌ কসরতের কোনো প্রয়োজন নেই। হাঁটা একদম সহজ। কিন্তু এ স্যুট তাকে শুধু বাড়ি থেকে যোজন যোজন দূরত্বের কথাই মনে করিয়ে দেয়নি, বরং সময় থেকেও যেন এগিয়ে দিয়েছে অনেকটা। এর বাড়তি ওজনটা একটু হলেও পৃথিবীর বুকে ওজনের কথা মনে করিয়ে দেয়।
এক ঘণ্টার মধ্যেই আশপাশের দৃশ্য অনেক বদলে গেছে। চোদ্দদিনের চান্দ্র রজনী ফুরিয়ে গেছে প্রায়। করোনার দ্যুতি যেন মিথ্যা কোনো দৃশ্য। সবাইকে চমকে দিয়ে মাথার উপর শত ফুট উঁচু রেডিও মাস্টটা জ্বলতে শুরু করল লুকানো সূর্যের প্রথম আলোয়।
প্রজেক্ট সুপারভাইজার আর তার দুই চ্যালা এয়ারলকের ভিতর থেকে বেরুনোর আগ পর্যন্ত ফ্লয়েড আর তার সহকর্মীদের অপেক্ষায় ছিল। জ্বালামুখে পৌঁছতে পৌঁছতে এক অসীম ক্ষমতাধর সূর্য উঁকি দিল পুব দিগন্তের পেছন থেকে। ধীরে ঘোরা চাঁদের এপাশটায় সূর্যের উঠে আসতে আরো ঘন্টাখানেক লাগবে, এরি মধ্যে আকাশের তারারা হাপিস হয়ে গেছে।
জ্বালামুখ এখনো দিনের আলোর ছোঁয়া পায়নি, অভাবটা পুষিয়ে দিচ্ছে। চারপাশের ফ্লাডলাইটগুলো। ঢাল বেয়ে কৃষ্ণমূর্তির দিকে এগুতে এগুতে ফ্লয়েড শুধু অসহায় বোধ করেনি, একটু ভয়ও পাচ্ছে। হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু তার ভাবনা অন্য। এই রহস্যের সমা কোনোদিন মানুষ করতে পারবে? তিন মিলিয়ন বছর আগে কিছু একটা এখান দিয়ে গিয়েছিল। আর সে রহস্য এখনো স্থির, অবিচল। কীসের প্রতিক্ষায় আছে এটা?
চিন্তায় বাঁধা দিল স্যুট রেডিও, ‘প্রজেক্ট সুপারভাইজার বলছি, ডক্টর ফ্লয়েড, কয়েকটা ছবি তুলতে চাচ্ছি। একটু লাইন করে দাঁড়াবেন, প্লিজ? আপনি এই এখানটায়, মাঝখানে আসুন, ডক্টর মাইকেলস আসুন এদিকে…’
কেউ আশা করেনি ফ্লয়েড এখানেও মজার কিছু পাবে। কিন্তু যে ক্যামেরা এনেছে তার উপর সে মহাতুষ্ট। এ ছবি নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক হবে। সে তাই দাঁত কেলিয়ে হাসি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং ছবির কয়েকটা কপিও দাবী করেছে। আল্লা আল্লা করে হেলমেটের কাঁচের ভিতর দিয়ে চেহারা স্পষ্ট দেখা গেলেই হল।
‘থ্যাঙ্কস, জেন্টলমেন, বেসকে বলে দিব, সবাই কপি পাবেন।’
এবার ফ্লয়েড তার পুরো মনোযোগ দেয় নিরেট জিনিসটার উপর। পাক খায় চারধারে। তার মন কেন বোঝে না যে এরমধ্যে নতুন কিসসু পাওয়ার নেই। এ জিনিসের প্রতি বর্গ ইঞ্চি চষে ফেলা হয়েছে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে।
এবার শম্বুক গতির সূর্য দেখা দিল জ্বালামুখের উপরে। এর অকৃপণ কিরণধারার প্রথম ছোঁয়া বর্ষিত হচ্ছে কৃষ্ণগাত্রে। এখনো পুরো আলোটা যেন টেনে নিচ্ছে আলো খাদক জিনিসটা।
একটা ছেলেমানুষি পরীক্ষা করার জন্য ফ্লয়েড দাঁড়িয়ে যায় সূর্য আর টি এম এ ১ এর মাঝামাঝি। তার ছায়া কি পড়বে জিনিসটার গায়? এটা যেন সূর্যের দিকেই তাক করা। না, ছায়ার নামগন্ধও নেই। কমপক্ষে দশ কিলোওয়াট নগ্ন আলো পড়ছে স্ল্যাবের উপর। ভিতরে কিছু থেকে থাকলে সেটার কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে সেদ্ধ হয়ে যাবার কথা।
কী অবাক ব্যাপার, আজ ফ্লয়েড এখানে দাঁড়িয়ে আছে, আর ত্রিশ লাখ বছরের মধ্যে এ জিনিস সূর্যালোকে নেয়ে উঠেছে আজই প্রথমবারের মতো। পৃথিবীতে বরফ যুগ আসারও আগে এ জিনিস শায়িত ছিল ভূগর্ভে। কালো রঙটা একদম আদর্শ। আর সূর্যের আলো শুষে নেবার জন্যও উৎকৃষ্ট পথ। সাথে সাথেই নিজের চিন্তাটা বাতিল করে দিল ফ্লয়েড। এই ধারণা দিয়ে লোকহাসানোর কোনো মানেই নেই। কোনো ব্যাটা এত পাগল হয়েছে যে সৌর শক্তিতে চলা কোনো বস্তুকে বিশ ফুট মাটির নিচে দাবিয়ে রাখবে!
সে মুখ তুলে তাকায় পৃথিবীর দিকে। উপভোগ করে দিনের কিরণধারা। ছ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই অসাধারণ আবিষ্কারের খবর জানে। চূড়ান্ত খবরটা বেরুনোর পর পৃথিবীতে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে?
চিরকালীন সব ভাবনা কেমন দুলে উঠবে! মানুষ, তার রাজনীতি, তার সমাজনীতি, তার সবকিছু হয়ে উঠবে দোদুল্যমান। প্রত্যেকে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোক, যে নিজের আশপাশে একটু হলেও তাকায় সে তার নিজের জীবন, মূল্যবোধ, দর্শন- সবই গোড়া থেকে কেঁপে উঠতে দেখবে প্রকটভাবে। এমনকি যদি তেমন কিছুই না পাওয়া যায় টি এম এ-১ থেকে, তবু এ এক অসীম রহস্য হয়ে টিকে থাকবে। মানুষ অন্তত এটুকু জানবে যে সেই একক বুদ্ধিমত্তা নয়। এ জিনিস চিরকাল মানুষের অসাধারণত্বের অহংবোধে খোঁচা দিয়ে যাবে। তারা সহস্র প্রজন্ম আগের হলে কী হবে, ফিরে আসতেও পারে। বিলুপ্ত হয়ে গেছে? ভালো, অন্য কেউ অবশ্যই থাকতে পারে অপার সৃষ্টিজগতের কোনো না কোনো কোণে। সারাটা ভবিষ্যৎ এই এক সম্ভাবনা বুকে নিয়ে বয়ে চলবে মানব সভ্যতাকে।
এসব ভাবনায় বেশ ডুবে ছিল ফ্লয়েড, কিন্তু এবারও বাগড়া দিল তার হেলমেট স্পিকার। অকল্পনীয় শক্তিশালী আর অপার্থিব শব্দ আসছে স্যুট হেলমেট থেকে। যেন চোখের সামনে কেউ চিরে দিল জগটাকে। শব্দটা অনেকটা ঘড়ির অ্যালার্মের মতো। সাথে সাথেই নিজের অজান্তে হেলমেটের উপর দিয়েই নিজের কানদুটো ঢেকে দেয়ার জন্য স্পেসস্যুট পরা হাত চেপে ধরে মাথার দুপাশে। এবার শব্দ কমানোর চেষ্টায় পাগলের মতো কোনো একটা সুইচ খুঁজছে ফ্লয়েড। দুলছে মাতালের মতো। একটু পরেই ক্ষমাসুন্দর নীরবতা নেমে এল চারদিকে। চারদিকের সবকিছু যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। রাক্ষসরাজ সোনার রথে চড়ে যাবার সময় পাথর করে দিয়ে গেছে আর সবাইকেও। তার মানে, আমার স্পেসস্যুটে কোনো সমস্যা হয়নিভাবে ফ্লয়েড। সবাই শব্দটা শুনেছে।
আর, ত্রিশ লক্ষ বছরের অমানিশা পার করে টি এম এ-১ স্বাগত জানালো।
স্বাগত জানালো চান্দ্র সূর্যোদয়কে।
অধ্যায় ১৪. শুনেছে যারা
শনির দশ কোটি মাইল পেছনের শীতল একাকিত্বে, যেখানে কোনো মানুষ কোনোদিন যায়নি, সেখানে ডিপ স্পেস মনিটর সেভেন্টি নাইন ধীর লয়ে ঘুরে চলেছে অস্টেরয়েড গ্রহাণুপুঞ্জের বেল্টের এবড়োখেবড়ো অবিটে। আপন মনে। তিন বছর ধরে এটা বেশ দক্ষতার সাথে আমেরিকান ডিজাইনার উদ্ভাবকদল, ব্রিটিশ নির্মাতা দল আর রাশিয়ান উৎক্ষেপণ বিজ্ঞানীদের সাফল্য ঘোষণা করছে। অ্যান্টেনার নাদুস-নুদুস জাল ছড়িয়ে থাকে এর চারপাশে। এগুলো সর্বক্ষণ চারদিকের সব বেতার তরঙ্গ, ভাঙনের শব্দ আর হিসহিসানি গলাধকরুণ করে। এই হিসহিসানিকেই অনেক বছর আগে প্যাস্কেল[২৭] বলেছিলেন ‘অসীম মহাকাশের নীরবতা’। গ্যালাক্সি বা আরো দূর থেকে আসা কসমিক রশিকে রেডিয়েশন ডিটেক্টরগুলো সব সময় রিসিভ ও অ্যানালাইজ করে। নিউট্রন আর এক্স রে টেলিস্কোপের দঙ্গল সব সময় এমন সব তারার উপর নজরদারি করে যেগুলো মানুষের চোখ দেখতে পায়নি কোনোকালে। ম্যাগনেটোমিটারগুলো সৌর বাতাসে হ্যারিকেনগুলোর ঘণ্টায় হাজার মাইল গতির বিশাল বিস্ফোরণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। দেখে নেয় সে সময়ে ঝড়ের মাঝখানে প্লাজমার ভয়াল খেলা। এই সব সহ আর যা ঘটে, তার সবকিছুর দিকেই ডিপ স্পেস মনিটর সেভেন্টি নাইন তার অক্লান্ত চোখ রেখেছে। সবটুকুই ক্রিস্টালাইন মেমোরিতে স্থান পায়।
এরই এক অ্যান্টেনা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখে দূরপ্রান্তে, সূর্যের কাছাকাছি। পৃথিবীর বুকে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর একটা করে পাঁচ মিনিটের রেডিও পালস সম্প্রচারিত হয়। ইলেক্ট্রিক মনিটর সারাক্ষণ যা দেখে তাই সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠিয়ে দেয়। আলোর গতিতে পনের মিনিট চলে তরঙ্গটা, পৌঁছে যায় ঠিকানামতো। সেখানকার মেশিন আর মেশিনম্যানরা তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষায় থাকে। তারপরই এমপ্লিফাই করে নেয় তথ্যটুকু। রেকর্ড হয়ে যায় হাজার হাজার মাইল লম্বা ম্যাগনেটিক টেপের গায়। টেপগুলো আছে ওয়ার্ল্ড স্পেস সেন্টার (ডব্লিউ এস সি) এর ওয়াশিংটন, মস্কো আর ক্যানবেরার শাখাগুলোয়। আর মানুষের দুনিয়াবী যন্ত্র এ সব ব্যাপার নিয়ে চর্বিতচর্বণ চালাতে থাকে।
প্রথম স্যাটেলাইট বসানো হয় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন, কোয়াড্রিলিয়ন কোয়াড্রিলিয়ন ইনফরমেশন পালস স্পেস থেকে অঝোর ধারায় ঝরছে সে সময় থেকেই। একটাই উদ্দেশ্য, মানুষের জ্ঞানটাকে আরেকটু এগিয়ে দেয়া। এসব বস্তাবন্দি জ্ঞান নিখুঁতভাবে দেখা হয়, তা না। এক মুহূর্তের কোনো বিশেষত্ব স্যাটেলাইটের চোখে পড়লেই যে তা মানুষের চোখে পড়বে, এমন নিশ্চয়তাও দেয়া যায় না। কিন্তু দশ, পঞ্চাশ বা শত বছর পর এ ডাটা কী কাজে লাগবে তা হয়তো এখন কল্পনা করাও অসম্ভব। সুবিশাল, প্রান্তহীন এয়ার কন্ডিশন্ড গ্যালারিতে তাই সারি সারি করে সব তথ্য জমা রাখা হয় পরম যত্নে। প্রতিটি তথ্যকে তিন কপি করে দেয়া হয় তিন সেন্টারে, নষ্ট হবার সম্ভাবনাকে পিছিয়ে দেয়া হয় আর একটু। এ হল পৃথিবীর সবচে দামী রত্ন, সমস্ত ব্যাংকের অযুত-নিযুত ভল্টে পড়ে থাকা অকর্মা সোনার তৃপের চেয়ে এর মূল্য অনেক বেশি।
আর এখন, ডিপ স্পেস মনিটর সেভেন্টি নাইন কোনো এক অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার লক্ষ্য করে ঘাবড়ে দিল সবাইকে। এক ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট বিশৃঙ্খলা সৌর জগতের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে। অতীতে কখনোই এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়নি। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটার দিক, সময়, প্রবণতা-সবকিছুই রেকর্ড করে নিয়েছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খবরটা পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে।
অরবিটার এম ফিফটিন দিনে দুবার মঙ্গলকে চক্কর দেয়। সূর্যের পথে ঘুরে চলছে হাই ইনক্লাইনেশন প্রোব টুয়েন্টি ওয়ান। ওদিকে পুটোরও পেছনে শীতল আবর্জনার মাঝে বিচরণরত কৃত্রিম উপগ্রহের নাম আর্টিফিশিয়াল কমেট ফাইড। এটা এত বিশাল অর্বিট ধরে ঘুরছে যেটা একবার ঘুরে শেষ করতে তার হাজার বছরেরও বেশি সময় প্রয়োজন। সবাই এই অতি কিম্ভুত শক্তি-বিস্ফোরণ দেখতে পেয়েছে। এ শক্তিধারা সেসব মহাকাশ দানোর কারো কারো কলকজায় নাকও গলিয়েছে। সব্বাই নিজ নিজ খবর সময়মতো স্টোর করে রাখবে পৃথিবীর বুকে, তিনটি সেন্টারে।
কম্পিউটারগুলো হয়তো কখনোই চার দূরবর্তী স্পেস-প্রোবের ব্যতিক্রমী তথ্য পাচারকে আলাদা হিসেবে ধরতে পারবে না। কিন্তু সকালে চিরাচরিত রুটিনে চোখ বুলাতে গিয়েই গদারের রেডিয়েশন ফোর্সকাস্টার বুঝতে পারল গত চব্বিশ ঘণ্টার কোনো এক সময় সৌর জগতের মাঝে কিম্ভুত কিছু একটা ঘটে গেছে।
সে শুধু এর পথনির্দেশের সামান্য অংশ বুঝতে পেরেছে। কম্পিউটার এ পথকে প্ল্যানেট সিচুয়েশন বোর্ডের উপর স্থাপন করতেই দেখা গেল মেঘহীন আকাশে স্পষ্ট একটা চিকণ মেঘরেখা। কিংবা বলা যায় কোনো কুমারী বরফভূমিতে একদল অবাঞ্ছিত মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েছে। এনার্জির কোনো এক অবস্তুগত আকৃতি। যেন কোনো গতিময় স্পিডবোট থেকে ছলকে উঠছে রেডিয়েশন। এর শুরু চাঁদের মুখে।
শেষ তারার দেশে।
৩. গ্রহগুলোর মাঝে
তৃতীয় পর্ব : গ্রহগুলোর মাঝে
অধ্যায় ১৫. ডিসকভারি
শিপটা সবে পৃথিবী থেকে ত্রিশ দিনের দূরত্ব পেরিয়েছে; কিন্তু এখনি ডেভিড বোম্যানের মনে হয় যেন সে কোনোকালে এ একাকী দুনিয়া ছাড়া আর কোনো বিশ্বে ছিল না। এই একলা পৃথিবীর নাম ডিসকভারি।
তার ট্রেনিংয়ের সবগুলো বছর; চাঁদ আর মঙ্গলের বুকে করা আগের যত্তসব অভিযান, তার বাদবাকি সব স্মৃতি যেন অন্য কারো, অন্য কোনো জন্মের কথা।
ফ্র্যাক পোল একই মতবাদে বিশ্বাসী। সে মাঝেমধ্যেই আফসোস করে, এটা মনোরোগ। আর এর চিকিৎসক এখান থেকে শত মিলিয়ন মাইল দূরে বসে। কিন্তু এই একাকিত্ব একদম ন্যায্য, এখানে কোনো অসুস্থতার চিহ্ন নেই। কারণটা সোজা, মানুষের মহাকাশ বিচরণের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এমন অভিযানের একটা নমুনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।
পাঁচ বছর আগে প্রজেক্ট জুপিটার আকারে এ মিশনের শুরু- গ্রহশ্রেষ্ঠের কাছে মানুষের প্রথম ধর্ণা দেয়ার চেষ্টা। দু-বছর ধরে শিপ প্রস্তুত হয়ে বসে থাকার পর হঠাৎ করেই মিশনের দিক বদলে গেল।
এখনো ডিসকভারি বৃহস্পতির দিকে যেতে পারে, কিন্তু থামবে না সেখানে। এমনকি বৃহস্পতি জগতের বিশাল উপগ্রহ-সাম্রাজ্যের কোথাও দৃষ্টিক্ষেপ করবে না মুহূর্তের জন্য, বরং গ্র্যাভিটিশনাল ফিল্ড কাজে লাগিয়ে নিজেকে সূর্যের কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে অনেক অনেক দূরে। সে নিজেকে বানাবে একটা উল্কা, তারপর সৌর জগতের ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে এগিয়ে চলবে বাইরের এলাকায়, নিজের চরম উদ্দেশ্যে। আঙটি পরা শনিগ্রহ তার আরাধ্য। সে আসবে না আর ফিরে।
ডিসকভারির জন্য এ এক ওয়ান ওয়ে জানি। তবু, এখনো এ মহাকাশ রথের ক্রুদের আত্মহত্যা করানোর কোনো মতলব আঁটা হয়নি। সব ঠিকঠাক চললে তারা ফিরবে আরো সাত বছর পর। এর মধ্যে পাঁচটা বছর চলে যাবে এক লহমায়, স্বপ্নহীন নিদ্রায়। এর নাম হাইবারনেশন, শীতন্দ্রিা। বাড়বে না বয়স তাদের। আসবে স্বপ্নের ডিসকভারি-টু। ঘুমের মধ্যেই তুলে নেবে তাদের দেবতার কল্পরথ।
‘উদ্ধার’ শব্দটা বেশ সতর্কতার সাথে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে সব অ্যাস্ট্রোনটিক্স এজেন্সির ডকুমেন্ট আর বিবৃতি থেকে। এই শব্দটা পরিকল্পনায় কিছু দুর্বলতা দুর্বলতা ভাব এনে দেয়। তাই বৈধ শব্দটা হল, ফিরিয়ে আনা। আসলেই, বিপদ হলেই না উদ্ধারের প্রশ্ন। আর বিপদ যদি হয়েই যায় তো পৃথিবী থেকে বিলিয়ন মাইল দূরে উদ্ধারের আশা তো বহুদূর, প্রশ্নই ওঠে না।
অজানার প্রতি আর সব অভিযানের মতো এটাতেও কিছু হিসেবনিকেশ করে বের করে নেয়া হয়েছে ঝুঁকির বাস্তব পরিমাণটা। অর্ধ শতাব্দীর গবেষণা আজ হাইবারনেশনকে করেছে পরিপূর্ণ, এর ফলেই মহাকাশ অভিযানের নতুনতম অধ্যায়ের সূচনা হয়। শুধু এ মিশন নয়, এর ফলে আরো অনেক মিশনের স্বর্ণদ্বার খুলেছে এই কল্পলোকের সোনার কাঠি-রূপার কাঠি।
সার্ভে টিমে আছে তিন সদস্য। এরা শনির চক্ৰবাকে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো কাজেই লাগবে না। তাই তাদের পুরো পথটায় ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। এর ফলে তাদের বয়স বেঁচে যাবে কয়েক মাস, বেঁচে যাবে টন টন খাবার আর দৈনন্দিন জিনিসপাতি। আরো বড় ব্যাপার হল, তারা দশ মাসের যাত্রা শেষে চরম বিরক্ত-অবসন্ন থাকবে না।
শনির একটা পার্কিং অর্বিটে ঢোকার তালে থাকবে ডিসকভারি। সে হবে দৈত্য গ্রহের নব অতিথি-উপগ্রহ। আজীবন ঘুরে চলবে বিশ লক্ষ মাইলের ডিম্বাকার পথ ধরে যেটা তাকে একবার শনির কাছাকাছি এনে ফেলবে, আরেকবার নিয়ে যাবে বেশ কয়েকটা উপগ্রহের পেছনে। কিন্তু তার আগে সে প্রথমে একটা চক্কর মারবে শনিকে। তারপর যাবে প্রত্যেক বড় উপগ্রহের অর্বিটে।
তাদের শত দিন পেরিয়ে যাবে পৃথিবীর চেয়ে আশি গুণ বড় দুনিয়া দেখতে দেখতে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো মুখিয়ে থাকবে পনেরটা পরিচিত উপগ্রহ, কে জানে, আরো উপগ্রহ আছে কিনা! তাদের একটা আবার আকার আকৃতিতে খোদ শুক্রের মতো বড়।
সেখানে নিশ্চয়ই শতাব্দী ধরে দেখার মতো সুযোগ পড়ে আছে। প্রথম অভিযানটা স্রেফ আবছা আবছা ধারণা দেবে। এখানে যা পাওয়া যায় তার সবটুকুই পাঠানো হবে পৃথিবীতে। অভিযাত্রীদল না ফিরুক, তাদের কাজ ঠিকই ফিরে আসবে।
একশো দিনের কাজ শেষে ডিসকভারি থেমে যাবে। সব কু চলে যাবে হাইবারনেশনে। নিতান্ত দরকারি সিস্টেমগুলো থাকবে সক্রিয়। দেখভাল করবে শিপের ক্লান্তিহীন ইলেক্ট্রনিক ব্রেন। তারপর সে এমন এক অতি পরিচিত অর্বিটে ঘুরপাক খাবে যেখানে হাজার বছর পরেও মানুষ তাকে খুঁজে নেবে সহজেই। কিন্তু প্রয়োজন মাত্র পাঁচটা বছর, তারপর খবরদারির দায়িত্ব নিচ্ছে ডিসকভারি-টু। এমনকি যদি ছ-সাত বা আট বছরও লেগে যায়, ঘুমন্ত সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা টের পাবে না। কারণ এরিমধ্যে হোয়াইটহেড, কামিনস্কি আর হান্টারের জন্য ঘড়ির কাঁটা থেমে গেছে।
বোম্যান ডিসকভারির ফার্স্ট ক্যাপ্টেন। মাঝে মধ্যে সে নিজের তিন সহকর্মীকে নিতান্তই হিংসা করে। হাইবারনেকুলামের বরফ শীতল নীরবতায় থেকে ওরা আর সবকিছু থেকেই দারুণভাবে মুক্ত থাকতে পারছে। ওদের কোনো দায়িত্ব নেই, জেগে ওঠার পর নেই কোনো একাকিত্ব।
কিন্তু এই বাহ্যিক দুনিয়া তাদের তদারকিতে ব্যস্ত। পাঁচটা ক্যাপসুলে পাঁচ নাম বোম্যান, পোল, হোয়াইটহেড, কামিনস্কি আর হান্টার। প্রথম দুটি ক্যাপসুল মৃত। আরো বছরখানেকের মধ্যে জীবিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনটা ছোট্ট সবুজ বাতি সারাক্ষণ জ্বালিয়ে রাখে; এর মানে-চিন্তা নেই, সব চলছে ঠিকঠাক। পাশে আছে খুদে ডিসপ্লে, সেই ডিসপ্লেতে দীর্ঘায়িত হার্টবিট, সামান্য পালসরেট আর সংকুচিত ব্রেন অ্যাকটিভিটি প্রকাশ পায়।
বোম্যান জানে, অপ্রয়োজনীয় একটা ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তাকে। আদৌ এমন পরিস্থিতি হবে না। যদি কখনো বিপদ ঘটে, তো লাল বাতি জ্বলবে, অ্যালার্ম বাজবে, সে শুনতে পাবে অতি ধীর লয়ের হৃদস্পন্দন। এমনকি সেই স্ক্রিনের উপর রেখাগুলো কী বোঝায় তাও সে জানে ট্রেনিংয়ের বদৌলতে।
সবচে ঝকমারি আর মেজাজ গন্ধ করা ডিসপ্লে হল ই ই জি স্ক্রিন। তিন ব্যক্তিত্বের এক স্থির, ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর। এটা একবারই স্থির হয়ে আছে, আবার চলবে তারা জেগে উঠলে। কিছুই যদি না দেখার থাকে তো কী দরকার ছিল এ জিনিসটা বসানোর? এখানে কোনো উঁচু-নিচু খাঁজ নেই। থাকবে কী করে, এটা জেগে থাকা মস্তিষ্কের অবস্থা বর্ণনা করে, বড়জোর স্বাভাবিক ঘুম। এ ঘুমে মস্তিষ্ক আদৌ কোনো উদ্দীপনা দেখাবে না। আর যদি কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যাপার ঘটেই, তা হবে যন্ত্র-এমনকি স্মৃতিরও অতীত।
শেষের ব্যাপারটা বোম্যান নিজেকে দিয়ে উপলব্ধি করেছে। মিশনের জন্য বেছে নেয়ার আগে তার হাইবারনেশন সক্রিয়তা মেপে দেখা হয়। সে বুঝতেই পারেনি জীবন থেকে একটা সপ্তাহ হারিয়ে গেল, নাকি সে সময়টা শুধুই শীতল মৃত্যুময় একটা অভিজ্ঞতা।
স্লিপ জেনারেটর চালু হওয়ার পর ইলেক্ট্রোডগুলো কপালে লাগানোর সাথে সাথেই সে কিম্ভুত কিছু আকৃতি দেখতে পায়, দেখতে পায় চলন্ত তারকা। তারপর সেগুলো মিইয়ে যায় এক সময়, আলোকহীনতা জাপ্টে ধরে অষ্টেপৃষ্ঠে। সে কখনোই ইঞ্জেকশনগুলো অনুভব করেনি, অনুভব করেনি শূন্যের মাত্র কয়েক ডিগ্রি উপরের শীতল তাপমাত্রা।
.
একসময় ডেভ বোম্যান জেগে ওঠে। জেগেই বুঝতে পারে, এইমাত্র তাকে শোয়ানো হয়েছে। কিন্তু সে জানত, এ এক মায়া; মিথ্যা ইন্দ্রজাল। বছর কেটে গেছে।
মিশন কি শেষ? তারা কি এখন শনিতে? কাজ শেষ করে ঘুমানোর পর ডিসকভারি-টু কি পৃথিবীর পথে তাকে বয়ে নিয়ে যাবে?
সে এক স্বপ্নময় ঘোরের দেশের বাসিন্দা। এখন আর সত্যি-মিথ্যা স্মৃতির কোনো তফাৎ করতে পারছে না। চোখ খোলার পর একদল মৃদুমন্দ আলোর ঝলক ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। এ সামান্য আলোই বহুক্ষণ তন্দ্রাহত করে রাখে তাকে। এবার বোম্যান বুঝতে পারে তার চোখ একটা শিপ সিচুয়েশন বোর্ডের ইন্ডিকেটরে আটকে আছে। কিন্তু এত অসম্ভব। কয়েক মুহূর্ত পরেই ধারণাটাকে বাতিল করে দেয় নিজে নিজে।
উষ্ণ বাতাস বয়ে যাচ্ছে গায়ের উপর দিয়ে। শরীরের তন্ত্রে তন্ত্রে জমে থাকা শতাব্দীর শীতলতাকে টেনে বের করে দিচ্ছে। চারদিক সুমসাম। শুধু মাথার পেছনের কোনো স্পিকার থেকে ঐন্দ্রজালিক সুরলহরী খেলে চলেছে ক্যাপসুল জুড়ে। ধীরে ধীরে এর তীব্রতা বাড়ে, বাড়ে মধুর ঝংকার।
এরপর একটা শান্ত, বন্ধুভাবাপন্ন কণ্ঠ ভেসে আসে। বোম্যান জানে সেটা কম্পিউটার জেনারেটেড ভয়েস।
‘তুমি কার্যকর হয়ে উঠছ, ডেভ। উঠে বসো না। নড়াচড়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কথা বলার চেষ্টা করোনা।’
‘উঠে বসো না!’ ভাবল বোম্যান। কী মজার কথা! একটা আঙুল নাড়ানোর ক্ষমতাও তার নেই। ঠাণ্ডা ভাবটা কাটেনি এখনো।
একটু পরে সে বেশ সন্তুষ্ট হয়। সে জানে রেসকিউ শিপ অবশ্যই এসেছে। একমাত্র সান্ত্বনা, অটোম্যাটিক ট্রিগারে যেহেতু চাপ পড়েছে, খুব শীঘ্রই সে মানবজাতির সদস্যদের দেখবে। ব্যাপারটা চমৎকার, কিন্তু কেন যেন খুব একটা উৎফুল্প বোধ করে না।
এখন খিদেটাই মূল ব্যাপার। কম্পিউটার অবশ্যই ব্যাপারটা বোঝে।
‘ডান হাতের পাশে একটা বোম দেখতে পাবে, ডেভ। খিদে পেয়ে থাকলে কষ্ট করে চেপে দাও।’
নিজের আঙুলগুলো নড়ানোর চেষ্টা করতে করতে সে ডানে একটা বাল্ব দেখতে পায়। বেমালুম ভুলে গেছে এর কথা। কিন্তু এ নিয়ে অবশ্যই তার বিস্তর পড়াশোনা ছিল! আর কী কী ভুলেছে ও? হাইবারনেশন কি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্মৃতিও ধুয়ে দিয়েছে?
এবার সে বাটনটা চেপে ধরে। কয়েক মিনিট পর একটা ধাতব হাত বাঙ্ক দিয়ে প্রবেশ করলে প্লাস্টিকের নিপল নেমে আসে ঠোঁটের দিকে। ব্যগ্রভারে সেটা শুষে নেবার সময় বোম্যান টের পায় পুষ্টিকর উষ্ণ তরল তার ভিতরটাকে আরো সতেজ করে তুলছে।
নিপলটা চলে যাবার পর আবারো বিরামের পালা। এবার হাত-পা বেশ নাড়ানো যাচ্ছেতো! এখন হাঁটা আর কোনো অবাস্তব স্বপ্ন নয়।
যদিও তার শক্তি ফিরে আসছে বেশ তাড়াতাড়ি তবু একটা চিন্তা পীড়া দিতে শুরু করল। চিরকাল এখানে শুয়ে থাকতে হবে যদি বাইরে থেকে কেউ না ওঠায়।
এবার আরেক কণ্ঠ কথা বলছে। পুরোপুরি মানবিক কণ্ঠস্বর। আর কোনো ইলেক্ট্রনিক মেমোরি নয়, নয় মানুষের-চেয়েও-বেশি-কিছু। এ কষ্ঠ পুরোপুরি পরিচিত, কিন্তু কে বলছে তা বোঝা দায়।
‘হ্যালো, ডেভ। ঠিক হয়ে যাচ্ছ বেশ দ্রুত। এবার কথা বলতে পার। তুমি কি জানো কোথায় আছ এখন?’
সে এ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মন খারাপ করে থাকে। যদি সত্যি সত্যি শনির চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে তো পৃথিবী ছাড়ার পরে এতগুলো মাসে কী হল? কবে ডিসকভারিতে উঠল? সব স্মৃতি কি শেষ? অ্যামনেসিয়ায়[২৯] ভুগছে নাতো? আবার বৈপরীত্য নিয়ে ভাবনা দেখা দেয়। যদি সে সহী-শুদ্ধভাবে অ্যামনেসিয়া শব্দটা মনে করতে পারে তো বাকী সব ভোলার যুক্তিটা কোথায়….
এখনো ডেভিড বোম্যান জানে না আসলে সে আছে কোথায়। কিন্তু সেপাশের কথক নিশ্চয়ই তার বেগতিক অবস্থা বুঝতে পারছে, ‘ভয় পাবার কিস্যু নেই, ডেভ। ফ্র্যাঙ্ক পোল বলছি। আমি তোমার হৃদপিণ্ড আর শ্বসন দেখছি। সব চলছে একদম ঠিকমতো। একটু বিরাম দরকার, বিশ্রাম নাও। এখুনি দরজা খুলে বের করে আনব তোমাকে।’
নরম আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চেম্বারটা। সামনে কিছু দেখতে পেল সে, সাথে সাথেই সবটুকু স্মৃতি ফিরে এল তড়িৎ গতিতে। এবার সে জানে ঠিক কোথায় আছে এখন।
ঘুমের দূরতম প্রান্তে আর মৃত্যুর নিকটতম সীমান্তে গেলেও কেটেছে মাত্র একটা সপ্তাহ। হাইবারনেকুলাম ছেড়ে যাবার পর শনির শীতল আকাশ দেখবে না, সেতো যোজন যোজন দূরে। সে এখনো গরম সূর্যের নিচে তপ্ত টেক্সাস শহরের হিউস্টন স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের ট্রেনিং কোর্সের একজন সদস্য।
অধ্যায় ১৬. হাল
কিন্তু এখন টেক্সাস আর নেই। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের খোঁজ লাগানোও নিতান্ত কঠিন। লো থ্রাস্ট প্লাজমা ড্রাইভ কতদিন আগেইতো বন্ধ হয়ে গেছে। ডিসকভারি আজো তার তীরের মতো শরীরটা নিয়ে পৃথিবীর দিকে পেছন দিয়ে সামনে এগিয়ে চলছে। নিরন্তর। তার সব অপটিক্যাল যন্ত্র বাইরের দিকের প্ল্যানেটগুলোর দিকে তাক করা, যেদিকে তার লক্ষ্য।
পৃথিবীর দিকে তাক করানো একটা টেলিস্কোপতো ছিলই। শিপের দৈত্যাকার লং রেঞ্জ অ্যান্টেনার প্রান্তে বসানো টেলিস্কোপটা যেন কোনো বন্দুকের দূরবীন। একটা ব্যাপার আগে থেকেই ঠিক করা, এই দানো-অ্যান্টেনা সব সময় তার দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট টার্গেটের দিকে ফেরানো থাকবে। এর ক্রসওয়্যারগুলোর কেন্দ্র একেবারে পৃথিবীর দিকে। যোগাযোগটা সজীব, সার্বক্ষণিক। যোগাযোগের অদৃশ্য সুতোর দৈর্ঘ্য বিশ লাখ মাইল; তার সাথে প্রতি মুহূর্তের দূরত্বও যুক্ত হয়।
প্রতি ওয়াচ পিরিয়ডে অন্তত একবার বোম্যান টেলিস্কোপটা দিয়ে আকাশ খুঁড়ে পৃথিবী বের করার চেষ্টা করে। এখন পৃথিবীটা সূর্যের অনেক কাছাকাছি চলে গেছে, তাই বসুন্ধরার কালো দিকটা সারাক্ষণ মুখ ব্যাদান করে থাকে ডিসকভারির দিকে। টেলিস্কোপের চোখে এখন গ্ৰহটার চন্দ্রকলার মতো গড়ন ধরা পড়ে, দেখায় আরেক শুক্রের মতো।
আস্তে আস্তে আলোর উৎস দূরে সরে যাচ্ছে, তারই সাথে সরে যাচ্ছে অন্ধকার গ্রহ, সেটাকে তুলে আনতে হয় টেলিস্কোপে। এ এক মহা ঝামেলা। কিন্তু টেলিস্কোপের দৌড়ও কম না, সে এই আঁধার পৃথিবীকেই যত্ন করে দেখিয়ে দেয়, রাতের আলোকোজ্জ্বল শহরগুলো কখনো দেখা যায় স্পষ্ট, কখনো বা আবহাওয়ার ধোঁয়াশায় আবছা হয়ে পড়ে।
এর মধ্যে আবার পিরিয়ডিক ব্যাপারও থাকে। চাঁদ একবার ভেসে চলে যায় পেছনে, একবার সামনে, তখন পৃথিবীর অনেক অংশই অদৃশ্য হয়ে পড়ে। তবে পূর্ণ চন্দ্র পৃথিবীর মহাসাগর আর মহাদেশগুলোকে আলোয় ভাসিয়ে তুলতেও দ্বিধা করে না।
এমন সব রাতে প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউগুলোও ধরা দেয় স্পষ্ট, দেখা যায় পরিচিত সব নৌবন্দর। চিরচেনা লেগুনের পাশে যে পাম গাছ তাকে ছায়া দিত সেগুলোর কথা মনে পড়ে খুব বেশি।
এখনো এ হারানো সৌন্দর্যের জন্য তার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। সে এই সৌন্দর্যের সবটুকুই চুটিয়ে উপভোগ করেছে পৃথিবীতে থাকার সময়। বোম্যান জানে, জীবনে পঁয়ত্রিশ বছরের দেখাই সব নয়; সে চায় ধনী হতে, চায় বিখ্যাত হতে, তারপর নতুন চোখ নিয়ে দেখতে চায় সেসব স্বর্গীয় সৌকর্য। স্বভাবতই দূরত্ব সেসবকে আরো আরো মূল্যবান করে তুলছে এখন।
তাদের ষষ্ঠ সদস্য এসবের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না। কারণ সে মানুষ নয়। সে হল অত্যাধুনিক এইচ এ এল নাইন থাউজ্যান্ড কম্পিউটার। হাল ন’হাজার হলো এই শিপের মস্তিষ্ক, ডিসকভারির স্নায়ুতন্ত্র।
হাল মানে হিউস্টিরিক্যালি প্রোগ্রামড অ্যালগরিদমিক কম্পিউটার। এ হল কম্পিউটার প্রজন্মের শেষ বিস্ময়, তৃতীয় প্রজন্ম[৩০]। এ প্রজন্মগুলোর কাল অতিবাহিত হয়েছে বিশ বছর পর পর।
প্রথম সাফল্য আসে উনিশশো চল্লিশ সালে। এনিয়াক[৩১] কম্পিউটারের বিকট বিকট ভ্যাকুয়াম টিউবগুলো নির্দ্বিধায় করে ফেলত হিসাবের হাজারো কাজ। তারপর উনিশশো ষাটের দিকে সলিড স্টেট মাইক্রো ইস্ট্রেনিক্সের[৩২] উদ্ভব। সে থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে অন্তত মানুষের সমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গড়ে তোলা সম্ভব। শুধু সময়ের প্রয়োজন। আর সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে দেয়ার মতো জায়গা যে কোনো ছোট ডেস্ক বা টেবিলেই পাওয়া যাবে।
সম্ভবত কেউ জানত না যে, এ হিসাবটার আর প্রয়োজন নেই, উনিশশো আশির দিকে মিনস্কি আর গুড[৩৩] দেখান, কী করে নিউরাল নেটওয়ার্ক[৩৪] গুলোকে স্বয়ংক্রিয় করে তোলা যায়। তারা সেই নেটওয়ার্কের স্বত:পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের রূপরেখাও তৈরি করার চেষ্টা করেন। বলেন যে এই সিস্টেম হবে মানুষেরই মতো ধীরে শেখা প্রোগ্রামযুক্ত, সে নিজে নিজে শিখবে।
কৃত্রিম মস্তিষ্ক মানুষের ব্রেনের চেয়ে অনেক দ্রুত অনেক বেশি তথ্য পাবে, শিখবে, জমা করবে। এর কাজের ধারা কখনোই বোঝা যাবে না। আর যদি যায়, তো সেটাও অন্য কোনো মেশিনের কাজ, কারণ এ ধারা মানুষের ব্রেনের ধারা থেকে লাখ গুণ জটিল হবে।
এর কাজ যেভাবেই হয়ে থাক না কেন, শেষ পরিণতি এই হাল। ফলে নতুনতর দর্শনের উদ্ভব হতে পারে, আসতে পারে নব দিগন্ত, যেখানে ‘শেখা’ শব্দটা আর ‘নকল করা’ কথাটার মধ্যে পার্থক্য পাওয়া যাবে। এখানে মানব মস্তিষ্কের প্রায় সব কাজই করা হবে, তফাৎ শুধু গতিতে। এ এক খরচান্ত ব্যাপার, আর তাই হাল ন’হাজার সিরিজের মাত্র কয়েকটা মেশিন তৈরি হয়েছে।
হাল তার মানব সাথীদের তুলনায় কোনো অংশে কম ট্রেনিং নেয়নি কারণ তার কোনো বিশ্রামের দরকার নেই। তার নেই মানুষের মস্তিষ্কের মতো সীমিত স্মৃতি ভাণ্ডার। এখানে হালের আসল কাজ লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম মনিটরিং করা। সারাক্ষণ অক্সিজেন, বাতাসের চাপ, জাহাজের খোলের ছিদ্র, রেডিয়েশন চেকিংসহ ভঙ্গুর মানব ক্রুদের জন্য আর যা যা করা দরকার– সেসব কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে তাকে। সে জাহাজের দিকনির্দেশও দিতে পারে প্রয়োজনমাফিক। হাল হাইবারনেটরদের দেখাশোনা করে, পাঠায় তাদের জীবন-অমৃত-তরল।
প্রথম জেনারেশন কম্পিউটারের ইনপুটে দরকার ছিল টাইপরাইটার অথবা কীবোর্ড, আর আউটপুট আসত প্রিন্টার-বড়জোর মনিটরে। প্রয়োজনে এ সব সুবিধাই হাল নিতে পারে, কিন্তু তার যোগাযোগ হয় কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে। বোম্যান আর পোল যখন খুশি হালকে মানুষ ভেবে কথা বলতে পারে। ইলেক্ট্রনিক ছেলেবেলার কয়েক হপ্তায় যে ইংরেজি শিখেছে সেই উচ্চারণে সে খুব সহজেই কাজ চালাতে পারে।
হাল নিয়ে মূল চিন্তা অন্যখানে, উনিশশো চল্লিশের দশকে ভুবনখ্যাত ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ অ্যালান তুরিং যা বলেছিলেন তা কি তার বেলায় প্রযোজ্য? তুরিং একটা মজার কথা বলেছিলেন। যদি একটা মেশিনের সাথে দীর্ঘসময় কথা বলা যায় হোক কীবোর্ড দিয়ে, হোক মাইক্রোফোনে-যদি মেশিনটা সেই সময় ধরে একজন বুদ্ধিমান মানুষের মতো কথা বলে যায় তবে সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। তবে তার সাথে বলা কথা আর প্রশ্ন তাকে শিখানো কথা আর প্রশ্ন থেকে কিছুটা হলেও আলাদা হতে হবে।
হাল এক তুড়িতে তুরিং টেস্ট পাশ করেছিল।
এমন সময়ও আসতে পারে যখন হাল নিজেই শিপের কমান্ড তুলে নিবে। যদি তার সিগন্যালের জবাব কেউ না দেয় জরুরী সময়ে, সাথে সাথে সে ঘুমিয়ে থাকা ক্রুদেরকে জাগানোর চেষ্টা করবে, তাতেও কাজ না হলে যোগাযোগ করবে পৃথিবীর সাথে, তার দাবী হবে পরের আদেশগুলো।
আর তাতেও কাজ না হলে নিজের হাতেই কমান্ড তুলে নিতে হবে, বাঁচাতে হবে শিপকে, চালাতে হবে মিশন। সেই মিশন-যার আসল উদ্দেশ্য কেবল সে জানে,
জানে না তার কোনো মানব কু।
বোম্যান আর পোল মাঝেমধ্যেই ঠাট্টা করে নিজেদেরকে এই শিপের সামান্য চাকরবাকর আর দারোয়ান বলে অভিহিত করে। তারা কল্পনাও করেনি তাদেরই রসিকতা কতটা নিষ্ঠুর সত্যি হয়ে দেখা দিতে পারে।
অধ্যায় ১৭. মহাকাশ বিহার
শিপের প্রতিদিনকার চলাচল খুব সতর্কতার সাথে বেছে নেয়া হয়েছে। আর তাত্ত্বিকভাবে বোম্যান ও পোল জানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিটি সেকেন্ড
তাদের কী কী করে কাটাতে হবে। তাদের কাজ বারো ঘণ্টা করে ভাগ করা। বারো ঘণ্টা একজনের ডিউটি চলবে, অন্যজনের বন্ধ। কখনোই দুজনে একসাথে ঘুমায় না। অফিসার অন ডিউটি থাকবে কন্ট্রোল ডেস্কে। অন্যজন টুকটাক কাজ করবে, দেখভাল করবে আশপাশটা, নয়তো বিশ্রাম করবে নিজের কিউবিকলে।
বোম্যান এ শিপের ক্যাপ্টেন হলেও বাইরে থেকে দেখে কেউ ব্যাপারটা ধরতে পারবে না। তারা এ সময়টায় সব কাজ ভাগ করে নেয়, নিজের পদমর্যাদাও বাদ পড়ে না।
বোম্যান দিন শুরু করে 0600 ঘণ্টায় সময়ের হিসাবটা অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল। মহাকাশবিদরা এক স্থির সময় নিয়ে নিয়েছে সারা সৃষ্টি জগতের জন্য-যাতে সময় নিয়ে ঘাপলা না বাঁধে। ক্যাপ্টেন দেরি করলেও সব সামলে নেয় হাল। জাগিয়েও দেয় তাকে। কিন্তু মিশনে নামার পর আর এর প্রয়োজন পড়েনি, একদিন পোল পরীক্ষা করে দেখার জন্য অ্যালার্মটা বন্ধ রেখেছিল, একচুল নড়চড় হয়নি বোম্যানের জেগে ওঠার সময়ে।
প্রথম কাজ হল হাইবারনেশন টাইমারটাকে আরো বারো ঘন্টার জন্য এগিয়ে রাখা। ঘুমন্ত ক্রুদের শীতনিদ্রা আরো বারো ঘণ্টার জন্য বেড়ে যায়। দুজনেই ভুলে বসলে হাল ধরে নেবে কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না, সে জরুরী পদক্ষেপ নেবে সাথে সাথে। এর কারণ অন্য কোথাও লুকিয়ে। হালকে দিয়েই এ কাজ করানো যেত। কিন্তু মিশনের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতারা চান সদা জাগ্রত কু দেখতে।
বোম্যান টয়লেট থেকে এসে চিরাচরিত ব্যায়াম সেরে নেয়। তারপর সকালের নাস্তা সারতে সারতে চোখ বুলায় ওয়ার্ল্ড টাইমসের সর্বশেষ রেডিও-ফ্যাক্সে। পৃথিবীতে থাকতে কস্মিনকালেও এত আগ্রহভরে সে সংবাদপত্র পড়েনি। এখন একেবারে সাধারণ সামাজিক গালগল্প আর রাজনৈতিক কচকচানিও তার চোখদুটোকে তন্দ্রাহত করে রাখে।
0700 বাজার সাথে সাথে সে আনুষ্ঠানিকভাবে পোলকে মুক্তি দেয়। সাথে দেয় একটা স্কুইজ কফি টিউব। সাধারণত রিপোর্ট করার মতো কোনো কিছু থাকে না। থাকলে সেটা সেরে নেয়। এরপর মনোযোগ দিতে হয় সব যন্ত্রাংশের পাঠে। ইন্সট্রুমেন্ট রিডিং শেষে কিছু টেস্ট সারার কাজ, এর ফলে অগ্রিম জানা যায় যন্ত্রপাতির হাল-হাকিকত। 1000টায় কাজ ফুরিয়ে যাবার কথা। তারপরই পড়ালেখার সময়।
সে জীবনের অর্ধেকটা পার করে দিয়েছে পড়তে পড়তে। অবসর পর্যন্ত তাই করতে হবে। বিংশ শতাব্দীর ট্রেনিং আর লার্নিং সিস্টেমকে অনেক ধন্যবাদ দেয়ার ইচ্ছা জাগে তার মনে। সে এরই মধ্যে দু-তিনটা কলেজের সমস্ত শিক্ষার সমান জ্ঞান অর্জন করেছে, আর মজার ব্যাপার হল, নব্বইভাগই তার মনে আছে।
অর্ধ শতাব্দী আগে হলে সে একই সাথে ফলিত মহাকাশবিজ্ঞান, সাইবারনেটিক্স আর মহাকাশ গতিবিদ্যার একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে সম্মান পেত। আর আজ নিজেকে যে কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দাবী করার ভাবনাটাকেও সলজ্জভাবে নাকচ করে দেয়। সে কোনোদিন একটা স্থির বিষয়ে মনোনিবেশের চেষ্টা করেনি। তাই নিজের শিক্ষকদের একদম হতাশ করে দিয়ে মাস্টার্সের বিষয় হিসেবে বেছে নেয় সাধারণ মহাকাশবিজ্ঞানের মতো একটা বিশাল, গাধা সাবজেক্টকে। এ বিষয়ের ছাত্ররা আই কিউর হিসাবে একশো ত্রিশের উপরে না যেতে পারলেও চলে, তারা সাধারণত কোনোদিন নিজের পেশার শীর্ষে যেতে পারে না।
অবশেষে তার পছন্দই ঠিক বলে বিবেচিত হয়েছে। কোনো এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হওয়ার কারণেই এখানে আসা সম্ভব হল। অন্যদিকে পোল নিজেকে ‘মহাকাশ জীববিদ্যার জেনারেল প্র্যাকটিশনার’ দাবি করে। এই দুজনের সাথে হালের অসীম স্মৃতি যুক্ত হয়ে মিশন পরিচালনাকে করে তুলেছে অপ্রতিরোধ্য।
1000 থেকে 1200 পর্যন্ত বোম্যান এক ইলেক্ট্রিক টিউটরের কাছে নিজের সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা দেয়, অভিযানের জন্য প্রয়োজন এমন সব কথা জেনে নেয়। সে পুরো শিপের প্ল্যান, সার্কিট ডায়াগ্রাম, অভিযান প্রোফাইল আর বৃহস্পতি-শনির পুরো উপগ্রহ জগতের ব্যাপারে নিজের জানাশোনা নিয়ে দাপড়ে বেড়াতে পারে সহজেই।
ঠিক দুপুরে, লাঞ্চের সময় এলেই নিয়ন্ত্রণ হালের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। লাউঞ্জ আর ডাইনিং স্পেসের জন্য এক রুমই বরাদ্দ। সেখানেও হুবহু একই রকম একটা সিচুয়েশন ডিসপ্লে প্যানেল আছে। হাল সারক্ষণ ওর সাথে যোগাযোগ রাখে। পোল তার ছ-ঘণ্টার ঘুমে যাবার আগে তার সাথে যোগ দেয়। এর সাথে প্রায় সব সময়ই থাকে পৃথিবীর বিভিন্ন টিভি প্রোগ্রাম।
মিশনের আর সব দিকের মতো তাদের খাবারের দিকেও সমান যত্ন নেয়া হয়। খাবারের বেশিরভাগই শুকনো। ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখা হয় এগুলোকে। এমন চমৎকার খাবার সৃষ্টিকুলে কেউ হয়তো পায় না; শরীরের সাথে ঠিকমতো খাপ খেয়ে যায়। প্যাকেট খুলে অটো গ্যালিতে ফেলে দিলেই হলো। সময়মতো রান্নাঘর জানিয়ে দেবে, দেখিয়ে দেবে সত্যিকার অরেঞ্জ জুস বা নানা ধরনের ডিম। আর কত ধরনের খাবারের কথা তারা মনে করতে পারে? সবই পাওয়া যাবে।
1300 থেকে 1600 পর্যন্ত শিপ ট্যুর। ডিসকভারি একপাশ থেকে আরেকপাশে প্রায় চারশো ফুট লম্বা। কিন্তু এর ক্রুদের রাজত্ব কেবল চল্লিশ ফুটের প্রেশার শরীরের ভিতর।
এখানে সব ধরনের লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম পাওয়া যায়। কন্ট্রোল ডেক হল শিপের হৃদপিণ্ড। এর নিচে আছে এক ছোট্ট স্পেস গ্যারেজ। ভিতরে তিন দরজা দিয়ে তিনটি অতি ছোট ক্যাপসুল ভেসে বেরিয়ে যেতে পারে। সেগুলো একজন মানুষের চেয়ে বেশি কিছু বয়ে নিতে পারবে না।
ডিসকভারির অক্ষে আছে পঁয়ত্রিশ ফিট ব্যাসের এক ড্রাম। সারাক্ষণ ঘোরে বলেই এখানে সৃষ্টি হয় একটু মাধ্যাকর্ষণ। চাঁদের মতো মাধ্যাকর্ষণ তোলার আশায় জিনিসটা সব সময় দশ সেকেন্ডে একবার ঘুরে চলে। ফলে নিতান্ত ওজনহীনতার ধকল থেকে বেশ ভালোভাবেই বেঁচে যায় ক্রুরা।
কয়রাসেলে আছে বেশ কিছু সুবিধা। কিচেন, ডাইনিং, ওয়াশিং আর টয়লেট রুমগুলো (অথবা বলা ভালো ব্যবস্থাগুলো) এখানে। একমাত্র এখানেই পানি ফুটানো নিরাপদ। অন্য কোথাও সে কাজ করতে গেলে পানির ভাসমান বুদবুদগুলো মহা তেলেসমাতি দেখাবে। দাড়ি কামাতে গিয়ে হাজারো টুকরোকে ভেসে বেড়াতে দেখতে হয় না। প্রান্তসীমা জুড়ে পাঁচটা ছোট্ট কিউবিকলে পাঁচ অভিযাত্রীর একমাত্র আপন ভুবন। তাদের মালসামানও সেখানেই থাকে। বর্তমানে মাত্র দুটি কিউবিক কাজে লাগছে।
প্রয়োজনে করোসেলের ঘূর্ণন থামানো যায়। সেক্ষেত্রে কৌণিক ভরবেগটা চলে যাবে একটা ফ্লাই হুইলে। কিন্তু থামানো হয় না কারণ এই ড্রামের ভিতর ঢোকা, সহজ। মই বেয়ে উঠতে হয়, সেখানে কোনো মাধ্যাকর্ষণ নেই। একটু চর্চা থাকলেই ব্যাপারটা কোনো চলন্ত এসকেলেটরে চড়ার মতো স্বয়ংক্রিয় হয়ে যায়।
আর শিপের লম্বাটে অংশটা চিকণ, তীরের মতো দেখতে। আর সব গভীর মহাশূন্যযানের মতো ডিসকভারিও মহা ভঙ্গুর বস্তু। এটা কোনো গ্রহের আকর্ষণ ক্ষেত্রেই প্রবেশ করতে পারবে না।
সে গঠিত হয়েছে পৃথিবীর অর্বিটে, তার পরীক্ষা হয়েছে একটু বাইরের দিকে, তার উৎক্ষেপণ হয়েছে চাঁদের বাইরের কক্ষপথে। সুতরাং সে মহাশূন্যের একেবারে খাঁটি সন্তান।
এই গোল মনুষ্য-এলাকার ঠিক বাইরেই রয়েছে চারটা বিরাট ট্যাঙ্ক। সেগুলো তরল হাইড্রোজেনে পূর্ণ। ট্যাঙ্কের পেছনেই এক মস্ত ভি অক্ষর, যেটা নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর থেকে বেরুনো বাদবাকি তেজস্ক্রিয়তা শুষে নেয়। এরপর রিয়্যাক্টর ঠাণ্ডা করার জন্য যে তরল প্রবাহিত হয় তার এক বিশাল, প্যাচানো লেজ। একে খুব সুন্দরভাবেই কোনো গঙ্গাফড়িংয়ের লেজের সাথে তুলনা করা যায়। এদিক দিয়ে ডিসকভারি যেন খানিকটা পুরনো দিনের জাহাজ।
ডি এর একদম শেষ মাথায় লুকানো আছে সেই প্রাণভোমরা, পারমাণবিক চুল্লী। এলাকাটা ক্রুদের কেবিন থেকে তিনশ ফুট পেছনে। এখানে আছে বেশ কিছু ফুয়েল রড, সেই রড ধারণ করে নক্ষত্র-অমৃত। প্লাজমা সৃষ্টি হয়, চলে যায় প্লাজমা ড্রাইভে। এর কাজ বহু হপ্তা আগেই ফুরিয়ে গেছে, সে ডিসকভারিকে চাঁদের পার্কিং অর্বিট থেকে ঠেলে বের করে দিয়েছে সাফল্যের সাথে। এখন প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ যোগান দেয়ার জন্য টিমটিম করে জ্বলছে এই চুল্লী। ভিটা এখন কালো আর ঠাণ্ডা। এটাই একেবারে গনগনে লাল হয়ে যায় পূর্ণ শক্তিতে প্লাজমা ইঞ্জিন চলা শুরু করার পর।
শিপের এসব এলাকায় যাবার কথা কস্মিনকালেও কেউ ভাবে না। এজন্য সদা সতর্ক থাকে রিমোট টিভি ক্যামেরাগুলো। বোম্যান ভালো করেই জানে যে সে প্রতি ইঞ্চি এলাকা চোখ বন্ধ করে বর্ণনা করতে পারবে।
1600’র মধ্যে কাজ শেষ করে মিশন কন্ট্রোলের জন্য রিপোর্ট পাঠাতে হয়। জবাব আসার পর নিজের ট্রান্সমিশন বন্ধ করে 1800 টায় পোলের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করার প্রস্তুতি নেবে।
তারা ডিউটির বাইরে ছঘন্টা সময় পায়। যা ইচ্ছা করে বেড়ানোর সেটাই আসল সময়। এর বেশিরভাগ কেটে যায় জাহাজের ইলেক্ট্রনিক লাইব্রেরিতে। বোম্যান সব সময় অতীতের বিশাল অভিযানগুলোর রোমাঞ্চ নিজের ভিতর অনুভব করে, সময়ের অনুপাতে সেসবের দূরত্বও ছিল কম। আজ সে স্বয়ং সবচে দূরবর্তী অভিযাত্রার যাত্রী।
কখনো বা সে হারকিউলিসের পিলার ছাড়িয়ে পাইথিয়াসে[৩৫] যাত্রা করতে উৎসাহী হয়। প্রস্তর যুগ থেকে মাথা ভাসানো আফ্রিকাকে সাগর তীর ধরে দেখার তার অদম্য স্পৃহা দেখার আশা জাগে দুই মেরু। অথবা দুহাজার বছর ফারাকে চলে গিয়ে সে ম্যানিলা গ্যালিয়ন[৩৬]গুলোতে চড়ে বেড়াতে চায় এ্যানসনকে সাথে নিয়ে। অথবা কুককে[৩৭] সঙ্গী করে পাল তুলে দিতে চায় শিহরণ ভোলা অস্ট্রেলীয় গ্রেট বেরিয়ার রিফের এলাকায়। সে ওডিসি[৩৮] পড়াও শুরু করেছে। সময় সাগর পাড়ি দিয়ে এই মহাকাব্যই তাকে বিস্ময়স্তম্ভিত করে রাখে।
বিশ্রামের জন্য সব সময় হাল তার সঙ্গী। গাণিতিক উপগাণিতিক গেমগুলো বেশ মজা দেয় তাকে। দাবা, চেকার্স, পলিওমিনাস গেমগুলো সব সময় খেলে তারা দুজন। হাল যদি নিজের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে খেলে, তাহলে কোনো মানুষের পক্ষে কখনোই জিতে যাওয়া সম্ভব হতো না। তাই এটাকে পঞ্চাশভাগ খেলা জেতার মতো করে প্রোগ্রাম করা হয়েছে। তার মানব সাথীরা এ খবর জানে না।
বোম্যানের শেষ ঘণ্টাগুলো খুচরো কাজেই ব্যয় হয়ে যায়, তারপর 2000 টায় পোলের সাথে ডিনার সেরে শুতে যাওয়া। এরপর একটা ব্যক্তিগত ঘণ্টা। পৃথিবী থেকে খবর নেয়া বা দেয়ার কাজে এটা খরচ করে ওরা।
অন্য সব সঙ্গীর মতো বোম্যানও অবিবাহিত। এত লম্বা অভিযানে বিবাহিত মানুষ পাঠাবার কোন যুক্তি নেই। অনেক সুকন্যাই তাদের ফিরে আসার আশায় দিন গুনবে বলে রেখেছে, কিন্তু কেউ কথাটা বিশ্বাস করেনি। তারা সপ্তাহে একবার পার্সোনাল কল করত, কিন্তু অপর প্রান্তে শোনার মানুষের কোনো অভাব ছিল না। আর এখন, অভিযানের শুরুর দিকেই মেয়েদের সংখ্যা কমতে শুরু করে। এমনই হবার কথা চিরকাল। তারা জানে। এ হল নভোচারীর চিরন্তন ভাগ্য, এমনই ছিল আগের দিনের পালতোলা জাহাজের বীর নাবিকের ললাট।
কথা সত্যি, সামুদ্রিক নাবিকেরা সাথী পেত, পেত ছোট্ট সব অভিযানের দায়িত্ব, সেগুলো বড়জোর বছরখানেকের মতো লম্বা। তাদের আছে অনেক অনেক নতুন নতুন বন্দর; দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, পৃথিবীর অর্বিটে কোনো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চমৎকার। দ্বীপদেশ নেই। স্পেস মেডিকরা এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে যথাসাধ্য করেছে।
একেবারে শেষ মুহূর্তে বোম্যান তার ফাইনাল রিপোর্ট জমা দেয়, চেক করে নেয় হালের টেপগুলো। তারপর মন চাইলে কয়েক ঘণ্টা বই পড়া বা চলচ্চিত্র দেখা। মাঝরাতে ঘুমাতে গেলে তার সাধারণত ইলেক্ট্রোনারকোসিসের সহায়তার প্রয়োজন পড়ে না।
পোলের কাজটাকে বলা চলে বোম্যানের কাজের প্রতিচ্ছবি। তারা দুজনেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান, স্থির চিন্তার অধিকারী এবং নিয়মানুবর্তী। তাদের মধ্যে কাজে গাফলতি বা ঝগড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। মিশন চলতে থাকে নিজের মতো।
ডিসকভারির ক্রুদের একটাই প্রত্যাশা, আগামী দিনগুলোতেও যেন এই রুটিনের কোনো ব্যত্যয় না হয়।
শুধু সময়ই এর জবাব দিতে পারে।
অধ্যায় ১৮. গ্রহাণুপুঞ্জের ভেতর দিয়ে
সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটা পথচলতি গাড়ির মতো ডিসকভারি নিজের অতি পরিচিত পথ আর অর্বিট ধরে এগিয়ে চলে। কিছুদিন আগে সে পেরিয়ে এসেছে মঙ্গলের কক্ষপথ, এগিয়ে যাচ্ছে বৃহস্পতির দিকে। পৃথিবীর সাগর আর আকাশে চলা অন্য লাখো শিপের সাথে তার এক বিরাট তফাৎ আছে। সে তাদের মতো প্রতি মুহূর্তে শক্তি ব্যয় করে চলে না। কাজে লাগায় গ্রহগুলোর গ্র্যাভিটিশনাল ফোর্সকে, মেনে চলে মহাকর্ষের অমোঘ কানুন। কোনো ডুবো চর বা পর্বত চূড়ায় ধাক্কা খাবার সম্ভাবনা নেই, নেই অন্য কোনো বাহনের সাথে সংঘর্ষের আশঙ্কা। কারণ মঙ্গলের পর থেকে অসীমে মিলিয়ে যাওয়া তারার দলের মধ্যে কোথাও মানুষের তৈরি কোনো যান চলছে না।
কিন্তু সামনে একটা নো ম্যান্স ল্যান্ড পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। দশ লাখেরও বেশি গ্রহাণু এ পথ ধরে বিচরণ করে। এদের মধ্যে বড়জোর দশ হাজার খণ্ডকে পৃথিবীর মহাকাশ বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি চিনতে পেরেছে, জানতে পেরেছে তাদের গতিপথ। তাদের মধ্যে মাত্র চারটির ব্যাস একশো মাইলের চেয়ে বেশি। পরিমাণে সবচে বেশি যারা আছে তারা হল মাঝারি আকারের পাথর-চাকতি। এরা এলোমেলোভাবে ভেসে বেড়ায় স্পেসের বুকে।
একদম ছোট্ট একটা গ্রহাণুও শিপটাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু এদের নিয়ে কিছু করার নেই। সাধারণত হাজার মাইলের মধ্যে একটা অ্যাস্টেরয়েড খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুবই কম। কোনো এলাকার দশ লাখ মাইলের মধ্যে গড়ে মাত্র একটা গ্রহাণু পাওয়া যেতে পারে।
ছিয়াশিতম দিনে তারা পরিচিত কোনো অ্যাস্টেরয়েডের সবচে কাছ দিয়ে যাবে। এর নাম নেই, সাধারণ একটা নাম্বার আছে-৭৭৯৪। পঞ্চাশ গজ ব্যাসের জিনিসটা সাতানব্বইতে চান্দ্র অবজার্ভেটরির চোখে প্রথম ধরা পড়ে। আবিষ্কারের পরপরই ব্যাপারটাকে ভুলে যাওয়া হয়, শুধু রেকর্ড থেকে যায় মাইনর প্ল্যানেট ব্যুরোতে।
কাছাকাছি আসার সাথে সাথে হাল বোম্যানকে মনে করিয়ে দেয় গ্রহাণুটার কথা। কিন্তু পুরো ভয়েজে এই একটা বাহ্যিক কাজই তার করার কথা, এটা কি ভোলা সম্ভব? অ্যাস্টেরয়েডটার গতিপথ, এর সবচে কাছে আসার মুহূর্ত, এর ছবি তোলার সম্ভাবনা-সবই ডিসপ্লে স্ক্রিনে উঠে পড়েছে। ৭৭৯৪ যখন তাদের মাত্র ন’শো কিলোমিটার দূর দিয়ে যাবে তখন তারা একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। দুজনের আপেক্ষিক গতি হবে ঘণ্টায় আশি হাজার মাইল।
বোম্যান হালকে টেলিস্কোপিক ডিসপ্লে দিতে বললে একটা নক্ষত্র-মানচিত্র ভেসে উঠল চোখের সামনে। এর মধ্যে কোনোটাকেই গ্রহাণুর মতো দেখায় না। টেলিস্কোপের সর্বশক্তি নিয়োগের পরও একেবারে মাত্রাহীন আলোর বিন্দু ছাড়া আর কিসসু চোখে পড়ে না।
‘টার্গেটের দিকে তাক কর।’
সাথে সাথে চারটি ক্ষীণ রেখা উঠে আসে। এরপর কিছু না দেখে যখন সে হাল ভুল করেছে ভেবে বসছে তখনি দূরের একটা আলোকবিন্দুকে নড়তে দেখা গেল। তারার জগত থেকে এক নক্ষত্র যেন এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। এটা এখনো হয়তো আধ মিলিয়ন মাইল দূরে।
ছ’ ঘণ্টা পর পোল তার সাথে যোগ দিল। এখন ৭৭৯৪ শত গুণ উজ্জ্বল। এত দ্রুত এগিয়ে আসছে যে তাকে দেখতে কারো অসুবিধা হচ্ছে না। এখন আর কোনো আলোকবিন্দু নয়, এগিয়ে আসছে এক স্পষ্ট চাকতি।
তারা যেন দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর ছোট্ট পাথুরে দ্বীপের দেখা পেয়ে আনন্দে আটখানা হওয়া কোনো বুভুক্ষু নাবিক। সবাই জানে এটা এক প্রাণহীন, বাতাসহীন পাথরের চাঙর, তাতে কী? আরো দু’শ মিলিয়ন মাইলের মধ্যে এই একটা জিনিসই দেখা যাবে। তারপর আছে বৃহস্পতির দুনিয়া।
গ্রহাণুটা বেটপ আকৃতির। একপাশ থেকে আরেকপাশে ঘুরছে, যেন বলছে, আমিও গ্রহ, মেনে চলি গ্রহের নিয়ম। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন অ্যাস্টরয়েডরা আসলে কোনো এক বিশাল গ্রহের ভগ্নাবশেষ। সেই গ্রহেরই কক্ষপথ ধরে অথৈ শূন্যতায় ঘুরে চলেছে আজো।
কখনো এটাকে মনে হয় সমতল কোনো চতুষ্কোণ বস্তু, কখনো বাঁকানো ইট আবার কখনোবা আরো বিকৃত। প্রতি দু-মিনিটের একটু বেশি সময়ে সেখানে একটা পূর্ণ দিন আর রাত পেরিয়ে যায়, অর্থাৎ একটা চক্র সম্পন্ন হয়। কখনো আলো ছায়ায় এক দুর্বোধ্য চিত্র সে, কখনোবা দ্যুতিময়।
তাদের পাশ দিয়ে গ্রাহক সেকেন্ডে ত্রিশ মাইল বেগে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখার জন্য তারা মাত্র কয়েকটা মিনিট হাতে পাবে। এর মধ্যেই ডজন ডজন ছবি তোলা হয়েছে, ভবিষ্যৎ অভিযানের জন্য শব্দের প্রতিধ্বনি নেয়া হয়েছে, আর পূর্ণ পরীক্ষা করার সুযোগ মিলেছে মাত্র একবার।
যে প্রোবটা পাঠানো হয়েছে সেটায় কোনো যন্ত্রপাতি নেই। এমন মহাজাগতিক গতিতে চলার সময় কেউ সংঘর্ষ সয়ে যেতে পারবে না। আসলে প্রোবটা হল এক টুকরো ধাতু, সেটাকে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে গ্রহাণুর দিকে।
ছুঁড়ে দেয়ার আগে দুজনে উত্তেজনার শেষ সীমায় চলে যায়, শত ফুটের কোনো টার্গেটে ঢিল ছোঁড়া কোনো ব্যাপার না হলেও হাজার হাজার মাইল দূর থেকে ঘণ্টায় আশি হাজার মাইল বেগে চলা লক্ষ্যে এমন কাজ চালানো …
অ্যাস্টেরয়েডের আঁধার অংশে বিশাল আলোর বিস্ফোরণ হয়। অপার্থিব গতিতে সংঘর্ষের কারণে প্রোবের অনেকটা ভর আর সবটুকু গতি পরিণত হয় তাপশক্তিতে। জ্বলন্ত বাস্পে ছেয়ে যায় আশপাশ।
ডিসকভারিতে সাথে সাথে ক্যামেরাগুলো বর্ণালী রেখার ছবি তুলে নেয়। পৃথিবীতে বসে বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে মাতামাতি করবে। এবং জ্বলন্ত পরমাণু ও অনুগুলোর খোঁজ পাওয়ার সাথে সাথে প্রথমবারের মতো গ্রহাণুর গঠন-উপাদানের কথা পৃথিবীর মানুষ প্রমাণসহ জানতে পারবে।
একঘণ্টায় আবার সেটা টিমটিমে তারায় পরিণত হলো, পরের বার বোম্যান খোঁজ করতে এলে সেটার কোনো চিহ্নই দেখাতে পারেনি হাল।
তারা আবার একা। তিনমাস পর আসছে গ্রহরাজ বৃহস্পতি।
অধ্যায় ১৯. বৃহস্পতির পথে
দু’কোটি মাইল দূর থেকেও বৃহস্পতিকে আকাশের সবচে উজ্জ্বল জিনিস বলে মনে হয়। এখনি গ্রহরাজকে স্নানভাবে আলো ছড়ানো স্যামন মাছের পেটের মতো দেখাচ্ছে। পৃথিবী থেকে চাঁদকে যেমন লাগে তার অর্ধেক আকৃতি পেয়ে বসেছে সে। বৃহস্পতির বাইরের জগতে রাজত্ব করছে চার উপগ্রহ আইও, ইউরোপা, গ্যানিমিড, ক্যালিস্টো। এ চারটা যদি বাইরে থাকত তবে নির্দ্বিধায় গ্রহ হিসেবে পরিগণিত হতো। কিন্তু দৈত্যাকার ম্রাট বৃহস্পতির কাছে এরা মামুলি প্রজা।
টেলিস্কোপে বৃহস্পতি এক বহুরঙা আকাশজোড়া গোলক হিসেবে ধরা দেয়। বারবার বোম্যান নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে এর ব্যাস পৃথিবীর চেয়ে এগার গুণ বড় আর এখন এ বিশালত্ব বুঝে ওঠার সাধ্য নেই তার।
নিজেকে হালের টেপ থেকে শিক্ষা দিতে দিতে হঠাৎ কিম্ভুত একটা ব্যাপার নজরে পড়ে যায়। অদ্ভুত একটা আকৃতি, এই বৃহস্পতির বুকেও পৃথিবীর বুকে ভারতের মতো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা।
ঠিকমতো টেলিস্কোপে বড় করে তুলে ধরার পর দেখা গেল জিনিসটাকে। বৃহস্পতির মহাঘূর্ণনের সাথে সাথে বিশাল মেঘমালা যেন ঘুরছে। কিছু ফিতার মতো এলাকাও চোখে পড়ে, সেগুলো গ্যাসের ঘূর্ণনে প্যাঁচ খেয়ে যায় মাঝে মাঝে। বাস্পের বিশাল দল উঠে আসে। এগুলোর কোনো কোনোটা আবার সিঁড়ির মতো একটা আরেকটার সাথে যুক্ত। সেসব সিঁড়িও অস্থায়ী। সেই মেঘমালার নিচে আর কী লুকিয়ে আছে? ভাবে সে, ভেবে নিজের ভিতরই হোঁচট খায়, আর কী লুকিয়ে থাকতে পারে?
এই চিরঘূর্ণায়মান বিশাল মেঘের ছাদের নিচে চিরদিনের জন্য আসল উপরিতলটা ঢেকে রাখে মহামতি বৃহস্পতি। তার রাজকীয়তার সাথে রাজকীয় গোপনীয়তাও স্পষ্ট। সেই মেঘের দেশে আবার কালো আকৃতি চোখে পড়ে, ভিতরের দিকের ছোট উপগ্রহগুলো কোনো কোনোটা ছায়া ফেলে মেঘরাজ্যের উপর।
সেখান থেকে বোম্যান বৃহস্পতির অন্যান্য উপগ্রহও দেখতে পায়। কিন্তু সেগুলো সামান্য উড়ন্ত পাহাড় ছাড়া কিছু নয়, মাত্র কয়েক হাজার কিলোমিটার তাদের ব্যাস। এবার শিপ তাদের কোনো একটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে। প্রতি মিনিটে রাডার তার শক্তি সঞ্চয় করে নীরব বজ্রাঘাত করবে সেসব উপগ্রহের গায়ে। শূণ্যতার মাঝ দিয়ে বেরিয়ে যায় তরঙ্গ, যেটুকু ফিরে আসে তা দিয়ে কোনো নতুন উপগ্রহের সন্ধান মেলে না।
বরং ফিরে আসে বৃহস্পতির গর্জনশীল রেডিও ভয়েস। উনিশশো পঞ্চান্ন সালকে বলা হয় মহাকাশবিদ্যার নবজন্মের কাল। তখন অ্যাস্ট্রোনোমাররা দেখতে পায় যে স্বয়ং বৃহস্পতি আকাশে লক্ষ লক্ষ হর্স পাওয়ারের দশ মিটার ব্যান্ড তরঙ্গ আকাশে ছুঁড়ে দিচ্ছে। অবিরত।
এর বেশিরভাগই খুচরো শব্দ, আবার কোনো কোনোটা পৃথিবীর ভ্যান এ্যালেন *বিশেষ টিকা দ্রষ্টব্য বেল্টের মতো কিন্তু তার চেয়ে অনেক অনেক বড় আর ক্ষমতাবান বৃহস্পতীয় বেল্টের তর্জন-গর্জন।
মাঝে মাঝে ভালো না লাগলে বোম্যান একা একা এসব শব্দে ঘর ভরে তোলে। এ যেন লক্ষ আতঙ্কিত পাখির চিৎকার। যেন কোনো নির্জন সমুদ্রতীরে উন্মাতাল ঢেউ ভাঙছে আর ভাঙছে, যেন কোন সে দূরের পথে একের পর এক বজ্রপাতের শব্দে ভরে উঠছে আশপাশ।
অসহায়ের মতো সে শোনে। তার করার কিছুই নেই।
ঘণ্টায় লক্ষ মাইলেরও বেশি গতিতে চলতে থাকা ডিসকভারি পুরো বৃহস্পতি জগৎ পেরুতে সময় নেবে দু হপ্তারও বেশি। সূর্যের অনুগত গ্রহের চেয়ে বৃহস্পতির অনুগত উপগ্রহের সংখ্যা বেশি। চান্দ্র অবজার্ভেটরি প্রতি বছরই একটা করে নতুন স্যাটেলাইট আবিষ্কার করত, ভাগ্য ভালো, এক সময় আবিষ্কার করাটা বন্ধ হয়েছে। হিসাবটা ঠেকেছে ছত্রিশ পর্যন্ত এগিয়ে। সবশেষ উপগ্রহের নাম বৃহস্পতি-পঁচিশ। সেটা এক কোটি নব্বই লক্ষ মাইলের অস্থিতিশীল কক্ষপথে তার সাময়িক দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে।
এ হল সূর্য আর বৃহস্পতির চিরকালীন দ্বন্দ্ব। সাধারণত বৃহস্পতিই বেশি এগিয়ে থাকে, তবে কয়েক মিলিয়ন বছরের মধ্যে অন্তত একবার বৃহস্পতির কোনো না কোনো উপগ্রহ হারিয়ে যায় গ্রহাণুপুঞ্জের মেলায়। শুধু বাইরের দিকের উপগ্রহগুলোই তার নিজের সম্পদ।
এবার অকল্পনীয় অভিকর্ষজ ক্ষেত্রের সাথে দুর্দান্ত একটা খেলা চলবে। ডিসকভারি এখন এগিয়ে যাচ্ছে একটা জটিল পথ ধরে। এ অর্বিট কয়েক মাস আগে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কারের পর হাল পরীক্ষা করে দেখেছে ভালোমতো। তাদের ট্রাজেক্টরির সাথে মানিয়ে নিতে প্রতি মিনিটেই কন্ট্রোল জেটকে চালাতে হবে।
পৃথিবীর সাথে সারাক্ষণ যোগাযোগ চলছে। তারা আজ পৃথিবী থেকে এত দূরে যে আলোর গতিতে সিগন্যাল আসতেও পঞ্চান্ন মিনিট সময় নিবে। তাই পুরো পৃথিবী তাদের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকলেও তারা যে খবরটা পাচ্ছে, যে দৃশ্যটা দেখছে তা একদম এক ঘণ্টার পুরনো।
প্রতিটা দৈত্যাকার ইনার স্যাটেলাইটের পাশ কেটে যাবার সময় টেলিস্কোপ মহাব্যস্ত হয়ে পড়ে। লাখো ছবি তুলে নিতে দ্বিধা করে না হাল। সেসব উপগ্রহের প্রত্যেকটা আকৃতিতে চাঁদের চেয়ে বড়। রহস্যে একেবারে আবৃত। ট্রানজিটের তিন ঘণ্টা আগে বৃহস্পতির আরেক উপগ্রহ ইউরোপার মাত্র বিশ হাজার মাইল দূর দিয়ে এগিয়ে যায় স্পেসশিপটি। সূর্যের দিকে হারিয়ে যাবার আগে সেটা ছিল পূর্ণ এক গোলক, তারো আগে চিকণ চাঁদের মতো দেখা দিয়েছিল। তার দিকে সব যন্ত্রপাতি চেয়ে ছিল বুভুক্ষের মতো। একদৃষ্টে। সেটার বুকে এককোটি চল্লিশ লাখ বর্গ মাইল এলাকা আছে। যে তথ্যগুলো টুকে নেয়া হচ্ছে প্রতি মিনিটে সেগুলো বিস্তারিত ভেঙে দেখতে হলে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে।
দূর থেকে ইউরোপা দেখতে যেন এক দৈত্যাকার তুষারের বল। দারুণভাবে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে যাচ্ছে সব সময়। কাছ থেকে দেখে বোঝা গেল যে ইউরোপা আসলে চাঁদের মতো ধূলিধূসর নয়, বরং বিরাট বিরাট হিমবাহের কল্যাণে তুষার শুভ্র। সেখানে অ্যামোনিয়া আর পানির কোনো অভাব নেই। বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ বল কীভাবে এগুলোকে একত্র করেছে কে জানে!
শুধু দুই মেরুতেই কোনো বরফ নেই। সেখানে নগ্ন পাথর বেরিয়ে আছে তাদের কালো মুখ ব্যাদান করে। কয়েকটা মৃত অগ্নিগিরিমুখ দেখা গেলেও আগ্নেয়গিরির কোনো লক্ষণ পাওয়া গেল না; ইউরোপার কোনোকালেই কোনো অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা উৎস ছিল না।
সেখানে বায়ুমণ্ডলের সূক্ষ্ম একটা লক্ষণ ধরা পড়ে। কোথাও কোথাও মেঘের ছোঁয়া। এ্যামোনিয়ার ধোয়া হতে পারে, মিথেন-বাতাসে এর জন্ম হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।
বৃহস্পতি এখন মাত্র দু-ঘন্টার পথ। হাল বারবার জাহাজের পথ দেখে নেয়। এখনো বিন্দুমাত্র সংশোধনের প্রয়োজন নেই। একটাই ভাবনা, বৃহস্পতি না টেনে নেয় তার অতল গর্ভে।
এবার অ্যাটমোস্ফিয়ারিক ভোব পাঠানোর পালা। আশা করা হয় এগুলো বেশ কিছুকাল টিকে থাকবে এবং খবরাখবর পাঠাবে পৃথিবী কিংবা ডিসকভারির বুকে।
দুটি বোমার আকৃতির বেঁটেখাট পোব ভদ্র মানুষের মতো ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ডিসকভারির অর্বিটে। সেগুলো কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত ডিসকভারির পেছন পেছন যাবে, আগুন যাতে না ধরে যায় তাই তার সাথে আছে হিট শিল্ড।
হাল নজরদারী করছে তাদের উপর। এবার শিপ যাবে বৃহস্পতির একেবারে নিকটতম অর্বিটে। এই কক্ষপথের ঠিক নিচেই বৃহস্পতীয় বায়ুমণ্ডলের শুরু। মাত্র কয়েক লাখ মাইলের ব্যবধানে এ কাজ সারা একেবারে ভয়াল বলা চলে, কারণ গ্রহটার ব্যাসই নব্বই হাজার মাইল। কিন্তু এ দূরত্বকে যথেষ্ট বলা যায়।
এবার পুরো আকাশ জুড়ে বসেছে গ্রহরাজ বৃহস্পতি। এর বিশাল আকার চোখও ধারণ করতে পারছে না, পারছে না মনও। চলছে মোহনীয় আলোর খেলা। লাল, হলুদ, গোলাপি, আর স্যামন রঙের হোলি না থাকলে বোম্যানের মনে পড়ে যেত পৃথিবীর আকাশের কথা।
আর, পুরো অভিযানে প্রথমবারের মতো তারা সূর্যকে আড়াল করতে যাচ্ছে। এখন সে অনেক ম্লান, অথচ সেই পৃথিবী থেকেই বিশ্বস্ত সফরসঙ্গী হিসেবে পথ দেখিয়েছে আলো দিয়ে। কিন্তু এবার অর্বিট ডিসকভারিকে টেনে নিয়ে যাবে বৃহস্পতির আড়ালে। এগিয়ে আসছে সেই রাত।
হাজার মাইল সামনে থেকে গোধূলীর বাঁক তাদের দিকে এগুচ্ছে তড়িঘড়ি করে। অন্যদিকে সূর্যটা বৃহস্পতির মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাবার পথে। এর আলো যেন কোনো জ্বলন্ত মহিষের উল্টো করা শিং। একটু পরেই বিনা প্রতিবাদে পাঁচ মাস পর ডিসকভারির আকাশ থেকে বিদায় নিল সৌর জগতের অধিকারী। রাত নেমেছে।
এখনো নিচের বিশাল সাম্রাজ্য পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। নিচে ফসফরাসের আলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। আলোর স্নান নদী প্রান্ত থেকে প্রান্তে বয়ে যাচ্ছে সবেগে। এখানে সেখানে তরল আগুনের মাতামাতি। বৃহস্পতির লুকানো হৃদয় থেকে উৎসরিত আলোময় গ্যাস ভাসিয়ে দিতে চায় চারদিক। পলক না ফেলে দেখার মতো দৃশ্য।
এগুলো খুবই সাধারণ কেমিক্যাল আর ইলেক্ট্রিক্যাল বিক্রিয়ার ফল, নাকি কোনো অপার্থিব প্রাণের পার্শ্ব-উপাদান? এই এক প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা তর্ক চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত কোনো অভিযান দিয়ে এর সমাপ্তি না ঘটে।
তারা বৃহস্পতির রাতের আরো ভিতরে যেতে থাকলে নিচের উজ্জ্বলতা আরো বেড়ে চলে। একবার অরোরার ডিসপ্লের সময় বোম্যান উত্তর কানাডার উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। সেই সুন্দর সৌর সৌকর্যময় এলাকায় বরফ থাকাতে আলোর দীপ্তি আরো বেড়ে যায়। কিন্তু তারা এখন যে এলাকায় ভেসে বেড়াচ্ছে সেটা একই রকম উজ্জ্বল হলেও শত ডিগ্রি নিচে হবে তার তাপমাত্রা।
‘পৃথিবীর সিগন্যাল দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে,’ বলল হাল, আমরা প্রবেশ করছি প্রথম ডিফ্রাকশন জোনে।
তারা জানে এমন হবে। তবু, প্রথমবারের মতো সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের একেবারে বিমূঢ় করে দেয় কিছুক্ষণের জন্য। রেডিও ব্ল্যাকআউট মাত্র একঘণ্টা চলবে। এই একটা ঘণ্টা তাদের জীবনের দীর্ঘতম প্রহরের মধ্যে অন্যতম।
অপেক্ষাকৃত কম বয়সের মধ্যেই পোল আর বোম্যান প্রায় এক ডজন মহাকাশ অভিযান সেরে ফেলেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ করে তাদের একেবারে নবীসের মতো লাগে। কোনোকালে এই গতিতে কোনো শিপ মহাকাশ ভ্রমণ করেনি। তারা বৃহস্পতির আকর্ষণকে দোলনা হিসেবে ব্যবহার করছে। একচুল এদিক-সেদিক হলে হয় সৌর জগতের বাইরে গিয়ে পড়বে, নয়তো গ্রহরাজের বুকে। দুটোই মৃত্যুর অপর নাম।
ধীর মিনিটগুলো কাটতে চায় না। এখন তাদের উপর বৃহস্পতি যেন ফসফরাস আলোর এক অসীম দেয়াল। এখনো বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে দৈত্যাকার গ্রহটা তাদেরকে উপগ্রহ বানিয়ে ফেলেনি।
অবশেষে, অনেক দূরে আলোর একটা ঝলক খেলে গেল। সেই একই মুহূর্তে হাল সগর্বে ঘোষণা করে উঠল, ‘আমি পৃথিবীর সাথে রেডিও যোগাযোগ করতে পেরেছি। একই সাথে আমরা এই জটিল পথপরিক্রমাও শেষ করেছি। শনির পথে আমরা চলব একশো সাতষট্টি দিন, পাঁচ ঘণ্টা, এগারো মিনিট।
ডিসকভারি অবশেষে বৃহস্পতির সদা চলনশীল গ্র্যাভিটিশনাল ফিল্ড থেকে মুক্তি পেল। এক ফোঁটা ফুয়েল না পুড়িয়ে সে বাড়িয়ে নিয়েছে প্রতি ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল গতি।
কিন্তু এখানেও প্রকৃতির সাথে কোনো জুয়া খেলা সম্ভব নয়। প্রকৃতি ডিসকভারিকে যতটুকু বাড়তি মোমেন্টাম দিয়েছে ঠিক ততটুকু কেড়ে নিয়েছে বৃহস্পতি থেকে। গ্রহটির ভরবেগ একটু হ্রাস পেলেও এর আকার ডিসকভারির তুলনায় কয়েক সেক্সটিলিয়ন গুণ বেশি হওয়াতে অর্বিটের স্থানচ্যুতি অসম্ভব কম। আজো সে সময় আসেনি যেদিন মানুষ তার কাজের ছাপ ফেলবে পুরো সৌর সাম্রাজ্যে।
আলো ফিরে আসতে আসতে পোল আর বোম্যান মহানন্দে পরস্পরের হাত ঝাঁকানো শুরু করে।
কিন্তু এখন আর তাদের বিশ্বাস হতে মন চায় না যে মিশনের প্রথম অংশটা মাত্র শেষ হল।
পুরোটাই পড়ে আছে সামনে।
অধ্যায় ২০. ঈশ্বরদের ভুবন
কিন্তু বৃহস্পতির সাথে তাদের লেনদেন শেষ হয়নি। অনেক পেছনে ফেলে আসা পোবদুটো ডিসকভারির সাথে লালচে দানবটার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছে।
একটা কোনো জবাবই পাঠায়নি। সম্ভবত ঢোকার পথেই জ্বলে গেছে। অন্য পোবটা একটু বেশি সাফল্য দেখানো শুরু করে। বৃহস্পতীয় আবহমণ্ডলের প্রথম স্তর ভেদ করে ভিতরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে বাইরে। পরিকল্পনামতো জিনিসটা এত বেশি গতি হারিয়েছে যে একটা বাঁকা পথ ধরে একে আবার বাইরে ফিরে আসতে হয়। দু-ঘণ্টা পর পোব গ্রহরাজের দিনের অংশে প্রবেশ করে ঘণ্টায় সতুর হাজার মাইল বেগে। সে এখন এক উপগ্রহ।
একটু পরই গ্যাসের একটা পাকচক্রে পড়ে গিয়ে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। ব্যগ্রভাবে অনেক মিনিট কাটানোর পর শিপের দর্শকরা নিশ্চিত হতে পারল না এ জিনিস আর কাজে লাগবে কিনা। সিরামিকের শিল্ডটা আবার যোগাযোগের আগেই পুড়ে গেলে সব আশা ভরসা ফুরিয়ে যাবে। কারণ ভিতরের যন্ত্রপাতির বাষ্পে পরিণত হতে দু-সেকেন্ড নাও লাগতে পারে।
কিন্তু শিল্ডটা কাজে লেগেছে। রোবট অ্যান্টেনা বেরিয়ে এসে উঁকি দিচ্ছে চারপাশে। প্রথম খবর পৌঁছতে পৌঁছতে ডিসকভারি চলে গেছে আড়াই লাখ মাইল দূরে।
প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার পালসের বর্ষণ হচ্ছে বৃহস্পতির আবহ থেকে। ঘোষণা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় সংযুক্তি, চাপ, তাপমাত্রা, চৌম্বকক্ষেত্র, তেজস্ক্রিয়তা সহ আরো শত শত জটিল অবস্থা যা শুধু পৃথিবীর বুকে বসে থাকা এক্সপার্টের দল বুঝতে পারবে। একটা রিপোর্ট সাথে সাথে বোঝা যায়, কারণ তা আসছে টিভি মনিটরে, পুরোপুরি রঙিন চিত্রে।
প্রথম চিত্রটা আসে রোবটের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে। শুধু হলুদ একটা ধোঁয়াশা চোখে পড়ে। ধোয়াটা অসীম কোনো অন্ত:সলিলা নদীর ঝর্নার মতো উঠে আসে উপরে। এদিকে রোবট প্রতি ঘণ্টায় কয়েকশ কিলোমিটার বেগে পড়ে যাচ্ছে ভিতরে।
আরো গম্ভীর হয়ে গেল কুয়াশা, এবার বোঝা দায় প্রোবের দৃষ্টিসীমা। সে দশ ইঞ্চি দেখছে নাকি দশ মাইল তা ঠাহর করা অসম্ভব। কারণ কোনো কিছুর দিকে ফোকাস করার উপায় নেই, আদৌ ফোকাস করার মতো কোনো জিনিসই নেই সেখানে। দেখে শুনে মনে হয় মিশনটা বৃথা গেল।
এরপর হঠাৎ করেই কুয়াশা সরে গেল। পোব কোনো এক ভারি মেঘের মধ্য দিয়ে শত শত মাইল পড়ার পর স্পষ্ট কোনো এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছে। সম্ভবত এটা খাঁটি হাইড্রোজেনের কোনো স্তর, ক্রিস্টাল অ্যামোনিয়াও হতে পারে। এখনো ছবিগুলো বোঝা দায়, এটুকু বোঝা যায় যে ক্যামেরার ফোকাস বেশ কয়েক মাইল দূরে।
এবার ছবি এত অপরিচিত যে পার্থিব দৃশ্যে অভ্যস্ত কোনো চোখ একে সয়ে নিতে পারবে না। অনেক অনেক নিচে স্বর্ণালী কোনো এক অবয়ব শুয়ে আছে, তার নেই কোনো সীমা, নেই কোনো শুরু। শুধু দেখা যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ। যেন দানবীয় সব পর্বতের চূড়া। কিন্তু সেখানে নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ নেই। সেই সোনালী এলাকাটা সমুদ্র না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু হতাশ হওয়া ছাড়া আর কী করার আছে, সামনের সেই অপার্থিব ভূমিও কোনো ভূমি নয়। এ হল বৃহস্পতীয় বায়ুমণ্ডল। সেটা মেঘের নতুন স্তর, ব্যস।
এরপর হঠাৎ করেই ক্যামেরা দারুণ অস্পষ্ট হয়ে যায়। কোনো এক অদ্ভুতুড়ের খোঁজ পেয়েছে সে। অনেক মাইল নিচে সেই সোনালী মেঘসমুদ্র আড়াল করে আছে এক চতুষতলকীয় জিনিস। সেটার সাথে কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপারের তুলনা করা যাচ্ছে না, যদিও এই স্বর্গীয় বিশালত্বে প্রাকৃতিক’ কথাটার মানেই পাল্টে যেতে বসেছে।
তারপর বায়ুচাপের কারণে প্রোবটা আরেক প্রান্তে চলে যায়। সেই কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিচে দ্রুত সরতে থাকা সোনালী এলাকাকে হলদেটে পর্দার মতো দেখায়। এবার পরীক্ষাযন্ত্র স্থির হলে ‘সমুদ্র’ আরো এগিয়ে আসে। কিন্তু এমন মহাকাব্যিক ছবি মানবজাতির কোনো সদস্য কোনোদিন দেখেনি। এবার দেখা যাচ্ছে কালো কালো সব গর্ত, সেগুলো দিয়ে নিশ্চয়ই আরো নিচের স্তরের ছবি তোলা সম্ভব।
সেখানে প্রোবের যাবার কথা নয়। প্রতি মাইলে প্রেশার বাড়ছে, বাড়ছে গ্যাসের ঘনত্ব, এগিয়ে আসছে রহস্য-জগতের কঠিন ভূমি।
জিনিসটার পুরো জীবন ক্ষয় করে হয়তো গ্রহপতির লাখো ভাগের এক ভাগও দেখা আর বোঝা সম্ভব হবে না, তাতে কী, এ সামান্য তথ্যও মানুষ তার মহাকাশবিদ্যার পুরো ইতিহাসে সংগ্রহ করতে পারেনি। তারপর আরো গম্ভীর হয় মেঘ, পোল আর বোম্যান নিজেদের চোখ আটকে রাখে টিভি স্ক্রিনের প্রতি।
প্রাচীনেরা নিশ্চয়ই বর্তমানের মানুষদের চেয়ে এ গ্রহ সম্পর্কে বেশি জানত। নাহলে কোনো দুঃখে ঈশ্বর রাজের নামে নাম রাখবে? যদি নিচে প্রাণ থেকেও থাকে তা খুঁজে পেতে কতদিন লাগবে? নাহয় গেল প্রাণী পাওয়া, আর কত শতাব্দীর দরকার এই মেঘমন্দ্র ঈশ্বরভূমিতে পা ফেলতে, কীরকম শিপ তৈরি করতে হবে সে কাজের জন্য?
কিন্তু আজ সেসব নিয়ে ডিসকভারি আর তার কুদের ভাবার অবকাশ নেই। তাদের লক্ষ্য আরো আজব এক গ্রহকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। আরো অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে পাঁচ কোটি মাইলের নিরেট শূন্যতা ভেদ করে সেখানে পৌঁছতে হবে।
৪. খাদ
চতুর্থ পর্ব : খাদ
অধ্যায় ২১. জন্মদিনের পার্টি
‘হ্যাপি বার্থডে,’ সেই চিরাচরিত চিৎকার ভেসে আসছে সাতশো মিলিয়ন মাইল : দূর থেকে আলোর গতিতে; ফুটে উঠছে কন্ট্রোল ডেকের ভিশন স্ক্রিনে। পোল পরিবার বেশ স্বার্থপরের মতো একত্র হয়েছে বার্থডে কেকের সামনে। হঠাৎ একদম নীরব হয়ে গেছে তারা সবাই।
তারপর মিস্টার পোল আনন্দের ভঙ্গী করে বললেন, ‘তো, ফ্র্যাঙ্ক, বলার মতো আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না এ মুহূর্তে পারছি শুধু এটুকু বলতে যে আমাদের চিন্তা চেতনা তোর সাথে সাথেই আছে। আর…উই আর উইশিং ইউ দ্য হ্যাপিয়েস্ট অব বার্থডেজ।’
‘নিজের যত্ন নিস, বোকা ছেলে,’ মিসেস পোলের কণ্ঠস্বর কেমন একটু বদলে যায়। তিনি কোনোদিন কান্না চাপতে শেখেননি, ‘খোদা তোর মঙ্গল করবেন।’
এরপর ‘গুড বাই’ এর একটা ঢেউ খেলে যায় পোল পরিবারের বাসায়। ভিশন স্ক্রিন কালো হয়ে গেলে নিজেকে নিজে বলে পোল, কী অবাক কাণ্ড, এসবই হয়েছে এক ঘণ্টারও বেশি সময় আগে। এতক্ষণে এই পুরো পরিবার যার যার মতো ছিটকে পড়েছে আশেপাশের কয়েক মাইল এলাকায়। এই সময়-পার্থক্য থাকার পরও মেসেজটা যেন ছদ্মবেশী কোনো আশীর্বাদ। আর সবার মতো সেও মনে মনে একটা দুঃখই পুষে চলে, যদি একবার সবার সাথে সরাসরি কথা বলা যেত। কিন্তু এই যে দৃশ্য, তা মোটেও বাস্তব নয়, মানসিক প্রভাবটাই প্রকট। সে আবারও দূরত্বের এক অতল গহ্বরে নিজেকে পড়ে যেতে দেখে, আর সব ভাবনা তলিয়ে যায় এর ভিতর।
‘উৎসবে নাক গলানোর জন্য দুঃখিত,’ বলল হাল, ‘কিন্তু আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি।’
একসাথে দুজনেই প্রশ্ন করে বসে, ‘কী সমস্যা?’
‘পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছি না ঠিকমতো। সমস্যাটা এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিটে। আমার সমস্যা প্রতিরোধ কেন্দ্র বলছে যে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে এটা নষ্ট হয়ে যাবে।’
বোম্যান ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিল, ‘আমরা এর দেখভাল করব। অপটিক্যাল অ্যালাইনমেন্টটা আগে দেখে নিই।’
‘এইতো, এটা, ডেভ। এ মুহূর্তে একদম ঠিকঠাক চলছে।’
ডিসপ্লে স্ক্রিনে একটা নিখুঁত অর্ধচন্দ্র দেখা দিল। তারাহীন আকাশের সামনে জিনিসটা একেবারে উজ্জ্বল দেখায়। তার পেছনে দীপ্তিময় আরেক পূর্ণগোলক। দেখে মনে হয় মেঘে ঢাকা শুক্র গ্রহ।
কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিতেই সে সম্ভাবনা নাকচ হয়ে যায়। শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই। দেখেই বোঝা যায় সেই দু-শরীর মা আর সন্তানের। এই ব্যাপারটা অনেক অ্যাস্ট্রোনোমার বিশ্বাস করতেন। পরে প্রমাণ হয় পৃথিবী আর চাঁদ কখনোই এক ছিল না।
আধ মিনিট সময় নিয়ে পোল আর বোম্যান ছবিটা খেয়াল করে দেখে। ইমেজটা লঙ ফোকাস টিভি ক্যামেরা থেকে আসছে। ক্যামেরাটা বড় রেড়িও ডিশে লাগানো, ডিশের রিমে বসানো, কারণ ডিশের মাঝামাঝি কিছু থাকলে খবর আদানপ্রদান সম্ভব হতো না। চিকণ পেনসিল বিমটা তাক করা থাকে পৃথিবীর দিকে, সেটা ডিশের মাঝে একমাত্র বৈধ দখলদার।
‘সমস্যাটা কোথায় তুমি কি জানো?’ প্রশ্ন করে বোম্যান।
‘বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত ভিতরে। এটুকু বলতে পারি যে প্রব্লেমটা এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিটেই।’
‘তুমি কোন্ সমাধান আশা কর?’
‘সবচে ভালো হয় বাড়তি ইউনিট দিয়ে বর্তমানটাকে বদলে দিতে পারলে। ভিতরে এনে আমরা সাথে সাথে চেক করতে পারব।’
‘ও কে, এবার অন্য কপিটা চাই।
তথ্যটা সাথে সাথে ডিসপ্লে স্ক্রিনে ফুটে উঠল। নিচের স্লটে পড়ে গেল একটা কাগজের টুকরো। আগে এই প্রিন্টআউটই ছিল একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু দিন বদলে গেছে।
এক মুহূর্ত ডায়াগ্রামটায় চোখ বুলিয়ে বোম্যান শীষ দিয়ে ওঠে।
‘তুমি হয়তো আমাদের বলছ যে, কথা বলার সময় ও একটু থামে, বাইরে যাওয়া উচিৎ।’
‘আই অ্যাম স্যরি। কিন্তু তোমরা তো জান যে এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিট অ্যান্টেনা মাউন্টিংয়ে বসানো।’
‘আমি সম্ভবত জানতাম। বছরখানেক আগের কথা। কিন্তু এই শিপে আট হাজার সাব সিস্টেম আছে। তার কোনোটা কোথায় সেসব মনে রাখা তোমার কম্ম, আমার নয়। বোঝা যাচ্ছে সমাধানটা একদম একরোখা, আমাদের বেরিয়ে গিয়ে নতুন ইউনিট বসাতে হবে, ব্যস।’
‘এ কাজ আমাকেই মানায়।’ বলল পোল। সে বাইরের কাজের জন্য ট্রেনিং নিয়েছে, কাজটা এক লহমায় করে ফেলতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, আমার কিছুই যায় আসে না।
‘আগে দেখে নিই মিশন কন্ট্রোল রাজি নাকি গররাজি।’ বলল বোম্যান, সে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে একটা মেসেজ পড়া শুরু করল নিজে নিজেই, কোনো কাগজ ছাড়া।
“মিশন কন্ট্রোল, দিস ইজ এক্স-রে-ডেল্টা-ওয়ান, অ্যাট টু-জিরো-ফোর-ফাইভ, শিপের নাইন-ট্রিপল জিরো কম্পিউটারের ভুল নির্ধারক সেন্টার দেখিয়েছে যে আলফা-ইকো থ্রি ফাইভ ইউনিট আর বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে নষ্ট হতে পারে। অনুরোধ করা হচ্ছে, আপনারা আপনাদের টেলিমেট্রি মনিটরিং করে শিপ সিস্টেম সিমুলেটরের রিভিউ ইউনিট দেখে নিন। আর ই ভি এ-তে গিয়ে এ ই থার্টি ফাইভ অপসারণের অভিযান অনুমোদন করে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। মিশন কন্ট্রোল, দিস ইজ এক্স-রে-ডেল্টা-ওয়ান, অ্যাট টু-জিরো-ফোর-সেভেন, ট্রান্সমিশন কনক্লুডেড।”
বহু বছরের সাধনার পর বোম্যান এই মান্ধাতা আমলের যোগাযোগ প্রক্রিয়া রপ্ত করেছে। এবার অপেক্ষা ছাড়া করার কিছুই নেই। দু-ঘণ্টারও বেশি সময় নেবে খবরটা আসতে।
বোম্যান যখন একটা জ্যামিতিক গেমে হালের কাছে হারতে বসেছে এমন সময় জবাব এলো।
‘এক্স-রে-ডেল্টা-ওয়ান, দিস ইজ মিশন কন্ট্রোল, আপনাদের তথ্য প্রাপ্তি স্বীকার করছি টু-ওয়ান-জিরো-জিরো-থ্রি-তে। আমরা টেলিমেট্রিক ইনফরমেশনে আপনাদের মিশন সিমুলেটর দেখছি। কাজ হলে উপদেশ পাঠানো হবে।
‘রজার[৩৮], ইউর প্ল্যান টু গো ই ভি এ অ্যান্ড রিপ্লেস আলফা-ইকো থ্রি-ফাইভ ইউনিট প্রায়োর টু পসিবল ফেইলুর। আমরা এর উপর টেস্ট চালাচ্ছি, রিপ্লেস করার ব্যাপারে অচিরেই তথ্য পাঠানো হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।’
সবচে বড় সমস্যা এবার কেটে গেল। টিকতে না পেরে কথক বিশাল মেসেজকে আর এই দাঁত ভাঙা ভাষায় না বলে সহজ ইংরেজিতে বলা শুরু করল।
“স্যরি, তোমরা একটু সমস্যায় পড়েছ। এটাকে তোমাদের কষ্টের সাথে যোগ করিয়ে দিতে চাই না। তোমরা যদি ই ভি এ-তে যেতেই চাও তো পাবলিক ইনফরমেশন থেকে একটা অনুরোধ ছিল। সবার কাছে পাঠানোর জন্য একটা ছোট্ট মেসেজ রেকর্ড করতে পারবে? বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটু কথাবার্তা, সাথে সাথে এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিট কী করে তা নিয়ে এক আধটু কথা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বললেই চলবে। বুঝতেই পারছ, যথাসম্ভব আশা দিতে হবে পাবলিকের মনে। ভালো হোক আর খারাপ, খবরটা একটু ভালোর দিকেই রেখ। আমরাও করতে পারি কাজটা, তবে তোমাদের মুখ থেকে না বেরুলে তোপের মুখেও পড়তে পারি। আশা করি এটা তোমাদের সামাজিক জীবনে তেমন নাক গলাবে না। দিস ইজ…”
আবার শেষকালের দাঁতভাঙা কথা।
অনুরোধ শুনে বোম্যান হাসবে না নাচবে তা ভেবে পায় না। এমন মাসের পর মাস কেটেছে যখন পৃথিবী তাদের খোঁজটুকুও নেয়নি। ‘খবরটা একটু ভালোর দিকেই রেখ…’ হাহ্!
ঘুমানোর আগে পোল তার সাথে যোগ দিলে দুজনে সেই মেসেজ লিখে অভিনয় করতে দশ মিনিট খরচ করল। প্রথম প্রথম হাজার হাজার অনুরোধ আসত; ইন্টারভিউ, আলোচনা, ব্যক্তিগত কথা, কত্ত কী! তারা কাশি দিতে চাইলে তাও একটা এক্সক্লসিভ খবর হয়ে যেত। সময় পার্থক্য মিনিট থেকে ঘণ্টার দিকে গড়িয়ে যেতেই আগ্রহ কর্পূরের মতো উবে গেছে। বৃহস্পতির পাশ দিয়ে উড়ে যাবার পর গত এক মাসে তারা মাত্র তিন-চারটা সাধারণ খবর পাঠিয়েছে সংবাদ সংস্থাগুলোর কাছে।
‘মিশন কন্ট্রোল, দিস ইজ…’ আপনাদের প্রেস রিলিজটা পাঠালাম।
‘আজ দিনের শুরুতে একটা ছোট টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের হাল ন’ হাজার কম্পিউটার আন্দাজ করে যে এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিট কোনো গণ্ডগোল পাকাচ্ছে।
‘কম্যুনিকেশন সিস্টেমের এ এক ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু এর গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের মূল অ্যান্টেনাকে এই জিনিসটাই পৃথিবীর সাথে গেঁথে রাখে। হাজার হাজার ডিগ্রির হিসাবেও এর সূক্ষ্মতা হ্রাস পায় না এক বিন্দু। সাতশো মিলিয়ন মাইল দূর থেকে পৃথিবী একদম নগণ্য এক তারা ছাড়া কিছু নয়। আমাদের পাতলা রেডিও বিম সহজেই গ্রহটাকে মিস করতে পারে।
‘অ্যান্টেনাটা সর্বক্ষণ পৃথিবীর দিকে তাক করা থাকে কারণ এর মোটরগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে মূল কম্পিউটার। কিন্তু সেই মোটরগুলো তাদের খবরাখবর পায় এই থার্টি ফাইভ ইউনিট এর মাধ্যমে। আপনারা একে কোনো শরীরের নার্ভ সেন্টারের সাথে তুলনা করতে পারেন। এই স্নায়ুকেন্দ্রই মস্তিষ্কের আদেশগুলোকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশীর উপযোগী করে অনুবাদ করে দেয়, দেয় পাঠিয়ে। আদেশ বয়ে না আনতে পারলে অঙ্গ একেবার অকেজো হয়ে যাবে। আমাদের ক্ষেত্রে, এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিট নষ্ট হলে অ্যান্টেনা যেমন খুশি তেমন ঘোরা শুরু করতে পারে, কিংবা পৃথিবীর দিকে তাক করা থাকলেও তার খবর চলে যেতে পারে হাজার গুণ দূর দিয়ে। গত শতাব্দীর গভীর মহাশূন্য অভিযানের সবচে বড় সমস্যার এও একটি।
‘আমরা এখনো ভুলটা ধরতে পারিনি; কিন্তু পরিস্থিতি মোটেও ঘোলা হয়ে যায়নি। আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। আমাদের হাতে আরো দুটি এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিট আছে। প্রত্যেকটি বিশ বছর কাজ করতে পারবে। এমনকি ভুলটা ধরতে পারলে প্রথম ইউনিটও ঠিক করা সম্ভব।
‘ফ্র্যাঙ্ক পোল এ কাজের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। তিনি বাইরে গিয়ে নষ্ট ইউনিটটার বদলে নতুনটা বসিয়ে আসবেন। এই সুযোগে তিনি শিপের গা পরীক্ষা করে ই ভি এ ইউনিটের বাকী জিনিসগুলোও দেখে আসতে পারবেন।
‘এই ছোট সমস্যা ছাড়া মিশন তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। আশা রাখি একই ভাবে বাকী সময় চলবে।
‘মিশন কন্ট্রোল, দিস ইজ এক্স-রে…’
অধ্যায় ২২. বেরিয়ে পড়া
ডিসকভারির বাইরের কাজ সারার জন্য যে ক্যাপসুল ব্যবহার করা হয় তার চলতি নাম ‘স্পেস পোড’। এগুলো নফুট ব্যাসের গোলক, ভিতরে বিশাল জানালা। পেছনে অপারেটর বসে। জানালার নাম বে উইন্ডো। মূল রকেট ড্রাইভটা মাধ্যাকর্ষণের পাঁচ ভাগের একভাগ আকর্ষণ তৈরি করে বেরিয়ে যায়। অন্যদিকে ছোট্ট অ্যাটিচ্যুড কন্ট্রোল জেটগুলো স্টিয়ারিংয়ের কাজ করে। জানালার ঠিক নিচে দুটি কৃত্রিম হাত বা ‘ওয়ালডো’ আছে যার একটা ভারি কাজ করে, অন্যটা একেবারে পল্কা কাজেও পটু। আরেকটা বেরিয়ে আসার মতো অঙ্গ আছে এই যানের, সেটায় ক্রু ড্রাইভার আর করাতের মতো অনেক যন্ত্র থরে থরে বসানো থাকে।
মানুষের সবচে আধুনিক যান নয় এই স্পেস পোড, তাতে কী, শূন্যে নির্মাণ বা বাহ্যিক কাজে এর জুড়ি মেলা ভার। সাধারণত তাদের মেয়েলি নাম থাকে, কারণ সম্ভবত এই যে তাদের কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাল্কা হলেও অপ্রতিরোধ্য, তাদের ছাড়া চলেও না। ডিসকভারির ত্রয়ীর নাম যথাক্রমে অ্যানা, বিটি আর ক্লারা।
একবার নিজের ব্যক্তিগত প্রেশার স্যুট গায়ে চাপিয়ে নিয়েই পোল পোডের ভিতর ঢুকে দশ মিনিট ধরে সেটার কন্ট্রোল দেখে নেয়। সব দেখে নিয়ে অক্সিজেন আর পাওয়ার রিজার্ভ পরীক্ষা করে। পুরোপুরি তুষ্ট হবার পর রেডিও সার্কিটে হালের সাথে যোগাযোগ করে। কন্ট্রোল প্যানেলে বোম্যান বসে থাকলেও কোনো বড়সড় ভুল না হলে তার নাক গলানোর নিয়ম নেই।
‘দিস ইজ বিটি। পাম্পিং শুরু কর।’
‘পাম্প করা শুরু হয়েছে।’
সাথে সাথে পাম্পের মৃদু আঁকি অনুভব করে পোল। যানটার গা একদম পাতলা। পাঁচ মিনিট পর হাল আবার খবর দেয়, ‘পাম্প করা সমাপ্ত।’
শেষবারের মতো পোল তার ছোট্ট ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল দেখে নেয়। সবই চলছে ঠিকমতো।
‘বাইরের দরজা খোল।’ সে আদেশ করে।
হাল কাজ শুরু করে দিয়েছে। যে কোনো কাজের যে কোনো পর্যায়ে পোল ‘হোল্ড’ শব্দটা বলা মাত্র সে কাজটা বন্ধ রাখবে।
পোডের সামনের দেয়াল চিরে যাচ্ছে। বাতাসের শেষবিন্দু মহাকাশে হারিয়ে গেলে পোল বুঝতে পারে ছোট্ট পোডটা একটু একটু কাঁপছে। দূরে ছোট্ট শনি দেখা যায়। এখনো চারশো মিলিয়ন মাইল যেতে হবে।
‘পোড বের কর।’
যে রেলের উপর পোড ঝুলছিল সেটা ধীরে বাইরের দিকে এগিয়ে যায়। ডিসকভারির বাইরে ছোট্ট স্পেসপোড বিটি ঝুলছে।
মূল জেটটা আধ সেকেন্ডের জন্য চালানোর সাথে সাথে রেল থেকে বেরিয়ে আসে বিটি। সে সূর্যের চারপাশে একান্ত নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরছে। এখন ডিসকভারির সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই, এমনকি নেই কোনো সেফটি লাইন-যেটা ধরে তাকে টেনে ভিতরে আনা সম্ভব। মাঝেমধ্যেই এই মরার পোডগুলো ঝামেলা পাকায়। অবশ্য তেমন কিছু হলে বোম্যান সাথে সাথে চলে আসবে।
বাইরের দিকে শ’ খানেক ফুট দূরে সেটাকে ভাসিয়ে নিয়ে পোল পরীক্ষা করে, সব ঠিকমতো চলছে। একবার পাশে, আর একবার পেছনে ঘুরিয়ে নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে কাজে মন দেয়।
প্রথম টার্গেট হল শিপের গায়ে আধ ইঞ্চি জুড়ে একটা নষ্ট এলাকা। পিনের মাথার চেয়েও ছোট্ট একটা ধূলিকণা তার অসীম বেগ নিয়ে এখানটায় আছড়ে পড়ার সাথে সাথে বাস্প হয়ে গেছে। কিন্তু রেখে যাওয়া ক্ষতচিহ্নটা কম কথা নয়। দেখে মনে হয় ভিতর থেকে কোনো বিস্ফোরণের জন্যে জিনিসটার এ হাল হয়েছে, আসলে গতিবেগের এ পর্যায়ে সাধারণ বিচারবুদ্ধি খুব একটা কাজে দেয় না।
পোডের জেনারেল পারপাস কিট থেকে একটা কন্টেইনার নিয়ে সেখানে বিশেষ একটা তরল ছিটিয়ে দেয় পোল। সাদাটে আঠালো জিনিসটা জ্বালামুখ ঢেকে দিল। প্রথমে একটা বড় বুদবুদ উঠল। পরে সব ঠিক হয়ে যাবার পরও পোল বেশ কয়েক মিনিট তাকিয়ে থাকে সেদিকে। তবু সতর্কতার খাতিরে আরেকবার স্প্রে করে অ্যান্টেনার দিকে মনোযোগ দেয়।
ডিসকভারির লম্বাটে শরীরের চারদিকে ঘুরতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে তার, কারণ সে কখনোই মিনিটে কয়েক ফুটের বেশি স্পিড় উঠাতে দেয়নি। শিপের শরীর থেকে বেরুনো কিম্ভুত যন্ত্রগুলোর সব ঠিক আছে কিনা তা দেখে নিয়ে সাবধানে চলতে শুরু করে। কারণ জেটের আগুন লেগেও শিপের ক্ষতি হতে পারে।
অবশেষে লং রেঞ্জ অ্যান্টেনার দিকে সে এগিয়ে যায়। বিশ ফুট ব্যাসের বিশাল ডিশটি যেন সরাসরি সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন পৃথিবী আর সূর্য এখান থেকে প্রায় একই দিকে দেখা যায়। বিরাট ধাতব চাকতির পেছনে ঢাকা পড়ে গেছে অ্যান্টেনা মাউন্টিং।
পেছন থেকে পোল এগিয়ে যায়। কারণ অগভীর প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টরের সামনে চলে গেলে যোগাযোগ কেটে যাবে সাময়িকভাবে। ছায়া সরিয়ে দিতে পোডের স্পট লাইট জ্বালিয়ে দিল পোল।
এই হালকা ধাতব প্লেটের পেছনেই যত অঘটনের নাটের গুরু বসে আছে। চারটা লকনাট আছে, খুলতে হবে। তবু পুরো এ ই পঁয়ত্রিশ ইউনিটটা বদলের সুবিধা রেখে তৈরি করা হয়েছে বলে সে তেমন ভ্যাজাল আশা করে না।
স্বাভাবিকভাবেই পোড়ে বসে কাজ সারা গেল না। একেতো যান্ত্রিকভাবে এ কাজ করে পোষাবে না, তার উপর মূল রেডিও মিররের কাগজ-পাতলা প্রতিফলন তল নষ্ট হয়ে যেতে পারে জেটের ছোঁয়ায়।
এই সব কাজই অপারেশনের আগে ঠিক করা। বোম্যান দুবার করে সব পরীক্ষা করে নিয়েছে। একে রুটিন চেকও বলা যায়। কিন্তু এই রুটিন চেকে একটু ভুল করলে তার কোনো ক্ষমা নেই, কারণ বাইরের অভিযানে কখনো ‘ছোট ভুল’ হয় না। যেটা হয় সেটাই বড়।
সে সময় মতো অ্যান্টেনা সাপোর্ট থেকে বিশ ফুট দূরে পোডটা নামিয়ে রাখল। শিপের গায়ের বাইরের দিকে যে মই লাগানো আছে তার গায়ে পোডের একটা হাত লাগিয়ে নিয়েছে, ভেসে যাবার ভয় নেই।
গায়ের স্যুটটা ভালোমতো পরীক্ষা করে নিয়ে সে পোড ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। বেরুনোর সাথে সাথে স্যুটের গায়ে দেখতে পায় ক্রিস্টাল বরফের পাতলা আবরণ। গায়ের বাতাসে লেগে থাকা পানির সবটুকুই জমে গেল। দূরের নক্ষত্রবীথি যেন আরো দূরে সরে গেছে।
বেরিয়ে যাবার আগে শেষ কাজ হিসেবে বিটির নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়াল থেকে বদলে দিয়ে রিমোট করে নেয়। এখন হালই বিটির নিয়ন্তা। তারপরও অতিরিক্ত সতর্কতা স্বরূপ তুলার চেয়ে একটু মোটা একটা কর্ডে নিজেকে বেঁধে নিয়েছে।
পোডের দরজা খুলে যাবার পর সে ধীরলয়ে বেরিয়ে পরে মুক্ত আকাশে। যানের বাইরে কাজ করার সময় কিছু নীতি মানতে হয়। সবকিছু সহজভাবে নাও-কখনো দ্রুত নড়ে না-থামো আর চিন্তা কর।
বিটির বাহ্যিক হ্যান্ডহোল্ড ধরে সে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চার মতো আটকে থাকা এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিট বের করে আনে। পোল পোডের কোনো খুচরো যন্ত্র ব্যবহার করবে না। এগুলো মানুষের হাতের উপযোগী নয়। বরং তার সব পছন্দের জিনিসই এখন কোমরে শোভা পাচ্ছে।
নিজেকে একটু ধাক্কা দিয়ে বিগ ডিশের পেছনে চলে গেলে তার দুটো ছায়া পড়ে, একটা সূর্যের আলোয়, অন্যটা বিটির স্পটলাইটের কল্যাণে। কিন্তু তার অবাক হতে বাকী ছিল। বিরাট আয়নার পেছনটাও ঝলমল করছে আলোতে। অতি ক্ষুদ্র আলোর রেখাও প্রতিসৃত হচ্ছে দারুণভাবে।
একটা মুহূর্ত স্তব্ধ থাকার পর ব্যাপারটা ধরা পড়ে। এই লম্বা ভ্রমণে কম মহাজাগতিক ধূলিকণার সাথে সংঘর্ষ হয়নি এই অ্যান্টেনার, সেগুলো অকল্পনীয় সূক্ষ্ম ছিদ্র তৈরি করেছে, সেখান দিয়েই আলো আসে। এরা সবাই এত ছোট যে সপ্রচার-কাজের কোনো ক্ষতিই হয় না।
ধীরে নড়তে নড়তে অ্যান্টেনা মাউন্টিংয়ের বাইরের দিকের হ্যান্ডহোন্ড ধরে নেয় সে। এরপর সবচে কাছের জায়গায় নিজের সেফটি বেল্ট লাগিয়ে নিয়ে রিপোর্ট করে বোম্যানের কাছে।
এই ছায়ায় ইউনিটটাকে দেখা যাচ্ছে না। তাই হালকে সেকেন্ডারি স্পটলাইট জ্বালাতে বলার সাথে সাথে ডিশের পেছনটা আলোয় ভরে গেল।
ধাতব শিটের উপর চোখ রেখে ঠাণ্ডা মাথায় ছোট্ট হ্যাঁচটার কথা ভাবতে ভাবতে আপন মনে বিড়বিড় করে ফ্র্যাঙ্ক পোল, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ইহা খুলিবার উপক্রম হইয়াছে, ফলে ইহার গ্যারান্টি নষ্ট হইবার পর্যায় উপস্থিত। জিরো টর্ক ক্রু ড্রাইভার দিয়ে সে প্রমাণ সাইজের গুলো তুলে আনে। এই বিশেষ যন্ত্রটার ভিতরের স্প্রিং সেই স্ক্রর বাইরের দিকের বল শুষে নেবে। তাই সেগুলোর উঠে গিয়েই ভেসে বেড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।
ক্রুগুলোকে তুলে নিয়ে পোল রেখে দিল কাজের পাউচে। এক সময় বলা হতো যে পৃথিবীর চারদিকে শনির মতো একটা বেল্ট তৈরি হবে। সেটায় থাকবে মহাকাশ নির্মাণের সময় ছিটকে পড়া বিভিন্ন বন্টু, খুচরো যন্ত্রাংশ, ধাতব টুকরো, অসাবধানে ফেলে দেয়া খাবারের ক্যান ইত্যাদি ইত্যাদি।
ধাতব ঢাকনাটা মহা গোঁয়ারগোবিন্দ। পোল একবার সন্দেহ করে বসে, সেটা হয়তো জাহাজের গায়ে পাকাপাকি বসিয়ে দেয়া হয়েছে। বেশ কয়েকবার জোরাজুরির পর ঢাকনা আলগা হয়ে আসা শুরু করে।
বিরাট একটা ক্রোকোডাইল ক্লিপ দিয়ে জিনিসটাকে সে অ্যান্টেনা মাউন্টিং এর সাথে আটকে রাখল।
এতক্ষণে সে ঠাণ্ডা মাথায় এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিটের ইলেক্ট্রনিক সার্কিটে চোখ বুলানোর ফুরসত পায়। জিনিসটা দেখতে পাতলা চারকোণা স্ল্যাবের মতো; আকৃতিতে মোটামুটি একটা পোেস্টকার্ডের মতো দেখায়। টেনে তুললেই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ উধাও হয়ে যাবে। ফলে তার উপরও অ্যান্টেনাটা এসে পড়তে পারে।
এজন্য প্রথমেই পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করতে হবে। এবার পোল অ্যান্টেনাটায় ধাক্কা না দিলে এম্নিতে নড়বে না। এই কমিনিটে পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলার তেমন সম্ভাবনা নেই।
রেডিওতে সে যোগাযোগ করল কম্পিউটারের সাথে, ‘হাল, এখনি ইউনিটটা সরাব। তুমি অ্যান্টেনা সিস্টেমের সব কনেল পাওয়ার অফ করে দাও।’
‘অ্যান্টেনা কন্ট্রোল পাওয়ার অফ।’
‘শুরু হচ্ছে, তুলে ফেলছি ইউনিট। এখুনি।’
কার্ডটা কোনো ভোগান্তির চেষ্টা না করে উঠে এলো। এর ডজন ডজন স্লাইডিং কন্টাক্টের কোনোটাই বিন্দুমাত্র গোঁড়ামী করল না। এক মিনিটের মধ্যে বাড়তি ইউনিটটা বসে গেল জায়গা মতো।
কিন্তু পোল কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। সে নিজেকে আস্তে করে অ্যান্টেনা মাউন্ট থেকে দূরে ঠেলে দেয়। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে হালকে কল করে, এবার নতুন ইউনিটের কাজ করার কথা। কন্ট্রোল পাওয়ার ফিরিয়ে দাও।’
‘পাওয়ার অন।’
অ্যান্টেনা একেবারে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।
‘ভুল পরীক্ষার টেস্টগুলো চালাও।’
এবার অনুবীক্ষণিক তরঙ্গ প্রবাহিত হলো ইউনিটের ভিতরে। সম্ভাব্য সব রকমের ভুল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রত্যেক যন্ত্রাংশের কাজ আর সহ্যক্ষমতা তলিয়ে দেখা শুরু করেছে হাল। এই কাজ আরো বহুবার করা হয়েছে ইউনিটটাকে ফ্যাক্টরি থেকে বের করার আগে। কিন্তু সেটা দু-বছর আর সত্তর কোটি মাইল দূরত্বের হিসাব।
‘সার্কিট পুরোপুরি অপারেশনাল,’ দশ সেকেন্ড পরেই হাল রিপোর্ট পাঠায়। এটুকু সময়ে সে এত বেশি টেস্ট শেষ করেছে যতটা কাজ করতে পারে ছোটখাট একটা সেনাবাহিনী কোনো সার্চ-অপারেশনের সময়।
‘চমৎকার।’ আনন্দিত গলায় বলে পোল, ‘এবার আমি কভার বসাতে যাচ্ছি।’
যানের বাইরের অপারেশনে এও এক ভয়াবহ কাজ। সাধারণত পুরো কাজটা সতর্কভাবে শেষ করে তারপর ফিরে যাবার মুহূর্তে কোনো ভুল করে বসে অভিযাত্রীরা। কিন্তু সে পৃথিবীর সেরা মহাকাশচারীদের একজন না হলে এ মিশনে স্থান করে নিতে পারত না।
সে সময় নিয়ে ভাবে। এরমধ্যে একটা স্ক্র বেরিয়ে গেল। কয়েক ফুটের মধ্যেই সেটাকে পাকড়াও করে নিল সে।
পনের মিনিট পর পোল ফিরে আসছিল স্পেস পোড গ্যারেজের ভিতর। তার মনে একটা তৃপ্তি কাজ করে, অন্তত একটা কাজ আর করতে হবে না।
দুঃখজনক হলেও সত্যি, তার ধারণাটা ভুল।
অধ্যায় ২৩. রোগ নির্ণয়
‘তুমি কি বলতে চাও যে,’ অবাক হওয়ার চেয়ে বেশি বিরক্ত হয়েছে পোল, ‘এই এত কাজ আমি করলাম তার সবই ফাও?’
‘অনেকটা তেমনই,’ পোলের ক্ষেপে যাওয়াটা কিঞ্চিৎ উপভোগ করছে বোম্যান, ‘পুরনো ইউনিটটা পুরোপুরি পাশ করে গেছে। এমনকি দু’শ পার্সেন্ট কাজ করানোর সময়ও কোনো সমস্যা করেনি।’
দু নভোযাত্রী তাদের ওয়ার্কশপ-কাম-ল্যাবে কাজ করছে। ল্যাবটা কয়রাসেলের ভিতর। পরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের জন্য এ জায়গাটা স্পেস পোড বের চেয়ে বেশি কাজে লাগে। এখানে কোনো জিনিসের হারিয়ে যাবার ভয় নেই, সূর্যকে ঘিরে পাক খাবার ভয় নেই, নভোচারীদের ভেসে যাবার ভয়ও নেই।
সেই পাতলা এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিটটা এক ম্যাগনিফাইং লেন্সের নিচে জবুথবু হয়ে পড়ে আছে। জিনিসটা এক ধাতব ফ্রেমে বসানো, ফ্রেম থেকে রঙ-বেরঙের তার বেরিয়ে গিয়ে টেস্টিং ইউনিটে জড়ো হয়েছে। অটোম্যাটিক টেস্ট সেটটা আকারে ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে মোটেও বড় নয়। কোনো ইউনিটকে পরীক্ষা করে দেখতে হলে শুধু ট্রাবলশুটিং’ লাইব্রেরি থেকে সঠিক কর্ডটা বেছে নিয়ে লাগিয়ে দাও, একটা বাটন টিপে বসে থাক, ব্যস। নষ্ট জায়গাটা ঠিক ঠিক দেখিয়ে দেবে ছোট্ট ডিসপ্লে মনিটর। এমনকি সমাধানও দেখিয়ে দেবে।
‘নিজে আরেকবার করে দেখ।’ একটু বিভ্রান্ত স্বরে বলল বোম্যান।
পোল ওভারলোড সিলেক্ট সুইচ অন করল। এক্স-টু দিয়ে টেস্ট বাটনে চাপ দিতেই স্ক্রিনে জল জুল করে উঠল, ইউনিট ওকে।
‘আমার মনে হয় আমরা এর উপর কাজের বোঝা চাপিয়ে যেতে পারি জ্বলে না যাওয়া পর্যন্ত, সে অনেকটা হতাশ কণ্ঠে বলল, তাতে কাজের কাজ কিসসু হবে কি?’
‘হালের ইন্টার্নাল ফল্ট প্রেডিকটর হয়তো কোনো ভুল করেছে।’
‘যাক, এসব বলে আর লাভ নেই। বরং খুঁতখুত করার চেয়ে বদলে দেয়া বহুৎ আচ্ছা। এ কাজে আমরা নিশ্চয়ই কোনো “কিন্তু” রাখতে চাই না?’
বোম্যান জবাব না দিয়ে জিনিসটাকে আলোয় তুলে ধরল। ছোট্ট একটা টুকরো। এর গায়ে অণুবীক্ষণিক সব জাল। দেখে শুনে একদম উচ্চস্তরের আর্ট বলে মনে হয়।
অনেকক্ষণ পর জবাব এল, “আমরা আসলেই কোনো কিন্তু রাখতে চাই না। হাজার হলেও এ জিনিসই আমাদেরকে পৃথিবীর সাথে গেঁথে রেখেছে। আমি এটাকে এন জি তে ফাইলবদ্ধ করে নষ্ট জিনিসের স্টোরে রেখে দিব। আমরা বাড়ি ফেরার পর কেউ না কেউ দামি জিনিসটা নিয়ে দুঃখ করতে পারে। আমাদের এসব মানায় না। আমাদের দরকার কিন্তুহীন মিশন।”
কিন্তু দুঃখিত হওয়া শুরু হয়েছে আরো অনেক আগে। পৃথিবী থেকে শেষ যে ট্রান্সমিশন হয় তখন থেকেই।
‘এক্স-রে-ডেল্টা-ওয়ান, দিস ইজ মিশন কন্ট্রোল, টু-ওয়ান-ফাইভ-ফাইভে বলছি, আমরা একটু সমস্যায় পড়েছি।
‘আপনারা রিপোর্ট করেছেন যে আলফা-ইকো থ্রি ফাইভ ইউনিটে কোনো সমস্যা নেই, আমাদের পরীক্ষণেও তা প্রমাণিত সত্য। সমস্যাটা সংযুক্ত অ্যান্টেনা সার্কিটে থাকতে পারে। কিন্তু যদি তা হয়ে থাকে তবে তার জন্য নতুনতর পরীক্ষণ প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয়।
‘তৃতীয় সম্ভাবনাও হিসাবে আনার যোগ্য। এটা আরো গম্ভীর হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট। (এতক্ষণে রিপোর্টার একটু বিরক্ত হয়েই যেন সাধারণ ভাষায় কথা শুরু করল…) তোমাদের কম্পিউটার ভুল করে থাকতে পারে। আমাদের নাইন ট্রিপল জিরোগুলোও একই তথ্য পেয়ে একই সাজেশন করছে। এ নিয়ে ঘাবরাবার কিছু নেই। কারণ, ব্যাক আপ সিস্টেম আছে। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের সতর্ক করা উচিত। পরে আর কোনো সমস্যা চোখে পড়ে কিনা দেখে নিও। আমরা গত কয়েকদিনে বেশকিছু ছোট ব্যতিক্রম পরীক্ষা করে দেখেছি। তাতে অবশ্য তেমন হেরফের হবে না। এসব থেকে কোনো উপসংহারেও পৌঁছতে পারছি না।
‘আমরা দুই কম্পিউটার নিয়েই পরীক্ষানিরীক্ষা করছি। ফলাফল পাবার সাথে সাথে তোমাদের জানানো হবে। আবারো বলছি, অ্যালার্মের কোনো প্রয়োজন নেই। বড়জোর তোমাদের নাইন ট্রিপল জিরোকে প্রোগ্রাম অ্যানালাইসিসের জন্য বিচ্ছিন্ন করা হতে পারে। তারপর কন্ট্রোলটা আমাদের অন্য কোনো কম্পিউটারের উপর ছেড়ে দিতে পারি। সময়-পার্থক্যটা সমস্যা করতে পারে, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এখনো পৃথিবীর কম্পিউটার দিয়ে শিপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কারণ তোমাদের ঘোঁট কম্পিউটারগুলো সময় পার্থক্য পুষিয়ে নিতে পারবে।
‘এক্স-রে-ডেল্টা-ওয়ান, দিস ইজ মিশন কন্ট্রোল, টু-ওয়ান-ফাইভ-সিক্স, সম্প্রচার সমাপ্ত।
পোল এই খবরটা আসতে দেখে নিরবে পরিস্থিতি যাচাই করা শুরু করল। আগে দেখা উচিত হালের কিছু বলার আছে কিনা, কিন্তু কম্পিউটার এই তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করার কোনো চেষ্টাই করেনি। ভাল; যদি হাল নিজে থেকে ব্যাপারটা না তোলে তো তার এ নিয়ে ঘাটাঘাটির দরকার কী?
আবার পালাবদলের সময় এসেছে, সে বোম্যানের জন্য অপেক্ষা করছে কন্ট্রোল ডেকে বসে থেকে। কিন্তু আজ সে প্রথমবারের মতো নিজের রুটিন ভেঙে বোম্যানের ঘরে গেল।
বোম্যান এরমধ্যে উঠে পড়েছে। ডিস্পেন্সার থেকে একটু কফি ঢেলে নিচ্ছিল এমন সময়ে একটু বিমর্ষ ‘গুড মর্নিং’ জানায় ফ্র্যাঙ্ক পোল। এত লম্বা মহাকাশ যাত্রার পরও তারা চব্বিশ ঘণ্টার দিনের কথা ভুলতে পারেনি যদিও তাদের কাছে রাতের কোনো ভূমিকা নেই।
‘গুড মর্নিং, কেমন চলছে কাজকর্ম?’
পোল নিজে একটা কফি নিয়ে প্রশ্ন করে, ‘মোটামুটি, তুমি কি ঠিকমতো জেগেছ?’
‘ভালই আছি। কেন, আবার কী হল?’
এর মধ্যেই দুজনে খুব সতর্ক হয়ে গেছে। রুটিনে একটু ব্যত্যয় ঘটলেই অন্যজন বুঝে নেয় কোনো সমস্যা আছে।
‘যাই হোক,’ ধীরে ধীরে বলে পোল, ‘মিশন কন্ট্রোল এইমাত্র আমাদের মাথায় একটা ছোটখাট বোমা ফেলেছে।’ সে কণ্ঠস্বর নিচু করে, যেন কোনো ডাক্তার তার রোগীর সামনে রোগ নিয়ে অন্য কারো সাথে কথা বলছে, সম্ভবত আমাদের শিপে হাইপোকন্ড্রিয়ার[৩৯] আলামত দেখা দিচ্ছে।
হয়তো বোম্যানের ঘুম পুরোপুরি কাটেনি। সে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় নেয় ব্যাপারটা বুঝে উঠতে গিয়ে। তারপর হঠাৎ করেই বলে ওঠে, ‘ও-আচ্ছা, আর কী বলল?’
‘বলল যে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কথাটা দুবার বলেছে। সম্ভবত প্রোগ্রাম অ্যানালাইসিস চালাবে।’
তারা দুজনেই জানে যে হাল প্রতিটি শব্দ শুনতে পাচ্ছে, সুতরাং এই ভদ্রোচিত পথ চলা ছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই। হাল তাদের সাথী, এ মুহূর্তে সেই সাথী নিয়ে একান্তে আলাপের পরিস্থিতি আসেনি।
তারা মিশন কন্ট্রোল থেকে পরের আদেশের অপেক্ষায় থাকে, হাল নিজেও কথাটা তুলতে পারে। যাই হোক, ডিসকভারির চেহারা পাল্টে গেছে। কোথাও যেন চিড় ধরেছে, বাতাসে স্তব্ধতার গন্ধ।
ডিসকভারি এখন আর কোনো সুখী শিপের নাম নয়।
অধ্যায় ২৪. ভাঙ্গা সার্কিট
আজকাল সবাই বলতে পারে কখন হাল কথা বলবে। প্রয়োজন ছাড়া সে আর টু শব্দটিও করে না। আগের মতো কথার আগে পরে বাড়তি ব্যক্তিত্ব জুড়ে দেয় না কম্পিউটারটা। গত কয়েক সপ্তাহে এই বিশেষ দিকটা আরো প্রকট হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা আরো বিরক্তিকর হওয়ার আগেই তারা কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ভাববে।
পোল ঘুমিয়ে ছিল, বোম্যান কন্ট্রোল ডেকে বসে পড়ার সময় হাল ঘোষণা করে, ‘ইয়ে, ডেভ, তোমার জন্য একটা মেসেজ ছিল।
‘কী?’
‘আমাদের আরো একটা এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিট নষ্ট হয়ে গেছে। আমার ফল্ট প্রেডিক্টর ইউনিট রিপোর্ট করেছে যে সেটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অকেজো হয়ে পড়বে।
বোম্যান বইটা নামিয়ে রেখে চিন্তান্বিত চোখে চেয়ে থাকে কম্পিউটার কনসোলের দিকে। সে জানে, ভালমতোই জানে যে ঠিক সেখানে হাল থাকে না, কিন্তু একে কী বলা যায়? কম্পিউটারের ব্যক্তিত্ব কোথায় থাকে? বড়জোর বলা যায় পরস্পর সংযুক্ত মেমোরি ইউনিটের গোলক ধাঁধা আর প্রসেসিং গ্রিডগুলোয় তার বাস। সেসব অংশ করোসেলের কেন্দ্রীয় অক্ষের কাছে অবস্থিত। কিন্তু একটা মানসিক ব্যাপার বলা চলে এই আচরণকে, ‘হাল’ বলতে ডেভ বোম্যান আর পোল তাকায় কম্পিউটার কনসোলের ক্যামেরার দিকে যেটা দিয়ে হাল তাদের দেখতে পায়।
‘আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না, হাল। দুদিনের মধ্যে দুটো ইউনিট নষ্ট হতে পারে না।’
‘আসলেই একটু অন্যরকম লাগে, ডেভ। কিন্তু তোমাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে সেখানে একটা সমস্যা হয়েছে।’
‘ট্র্যাকিং অ্যালাইনমেন্ট সিস্টেম দেখাও।’
ডেভ একেবারে ভালমতোই জানে যে এই দেখায় কিছু এসে যায় না। কিন্তু দেখাটাই আসল নয়, তার ভাবার জন্য সময় চাই। সেই সময়টা যাতে হাল না বুঝতে পারে। মিশন কন্ট্রোল যে রিপোর্ট পাঠানোর কথা বলেছিল তা এখনো এসে পৌঁছেনি। এবার একটু সাবধানে পরীক্ষা করার সময় এসেছে।
সামনে পৃথিবীর সেই পরিচিত দৃশ্য। এবার চাঁদ একটু পিছিয়ে যাওয়ায় সূর্যের আলোয় বসুন্ধরা দারুণ হাসি হাসছে। চিকণ পেন্সিলটা এখনো তাদেরকে উৎপত্তির গ্রহের সাথে আটকে রেখেছে। এই হওয়ার কথা। যোগাযোগ বন্ধ হলে অ্যালার্মের তারস্বরে চিৎকার করা ছাড়া উপায় থাকত না।
‘ভুলটা কোথায় তা নিয়ে তোমার কোনো ধারণা আছে?’
হাল কখনো এতক্ষণ চুপ করে থাকে না। অবশেষে সে জবাব দেয়, আসলে কোনো ধারণা নেই, ডেভ। আমার আগের রিপোর্টের মতো এবারো সমস্যার গোড়াটা ধরতে পারছি না।’
‘তুমি কি পুরোপুরি নিশ্চিত যে,’ খুব সাবধানে শব্দ খুঁজে বের করে বোম্যান, ‘যে…তুমি… কোনো ভুল হয়ে যায়নি…তোমার? জানোইতো, অন্য এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিটটা আমরা ভালমতো চেক করেছি। সেখানে কোনো সমস্যাই ছিল না।’
‘হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু এবার অবশ্যই ফল্ট আছে। সমস্যা ইউনিটে না থাকলে পুরো সাব সিস্টেমে আছে।’
বোম্যান কনসোলের উপর নিজের আঙুল দিয়ে বাজনা তোলে। এমন হতে পারে, যে পর্যন্ত একটা কাজ না হয় সে পর্যন্ত সমস্যাটার দিকেই হালের চোখ থাকবে।
‘ঠিক আছে, আমরা মিশন কন্ট্রোলকে ব্যাপারটা জানাই, তারপর দেখা যাক কী হয়…’ সে একটু থামলেও কোনো প্রতিক্রিয়া নেই হালের মধ্যে।
‘হাল,’ সে বলতে থাকে, ‘কোনো কিছু কি তোমাকে বিরক্ত করছে? এমন কিছু যা এর সাথে মিলে যায়?’
এবারও অস্বাভাবিক বিরতির পর হাল নিজের চির-স্থির কণ্ঠে বলে চলে, দেখ, ডেভ, আমি জানি তোমরা সাহায্য করার চেষ্টা করছ। কিন্তু আমি নিশ্চিত, ভুলটা হয় অ্যান্টেনা সিস্টেমে নয়তো তোমাদের টেস্ট প্রোগ্রামে। আমার ইনফরমেশন প্রসেসিং একেবারে ঠিকমতো চলছে। আমার রেকর্ড চেক করলেই দেখতে পাবে, সেখানে কোনো ভুলের নিদর্শন নেই।’
‘আমি তোমার সার্ভিস রেকর্ড সম্পর্কে সবই জানি, হাল। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় যে এবারও তুমি ঠিকমতো কাজ করছ। যে কেউ ভুল করতে পারে।’
‘আমি এ নিয়ে তর্কে জড়াতে চাই না, ডেভ, কিন্তু আমি ভুল করতে অক্ষম।’
এবার আর কোনো ভদ্র জবাব দেয়া যায় না, বোম্যান তাই কথাটাকে ছেড়ে দিল।
‘ঠিক আছে, হাল,’ সে একটু বেশি বন্ধুভাব দেখিয়ে বলে, ‘আমি তোমার দৃষ্টিকোণ বুঝতে পেরেছি। আমরা ব্যাপারটা সেভাবেই দেখব।’
সে যেন বলছে বাকী কথাটুকুও, প্লিজ, ব্যাপারটা ভুলে যাও। কিন্তু একমাত্র এ কাজটাই সম্ভবত হাল করতে পারবে না কোনোদিন।
মিশন কন্ট্রোল কখনোই যোগাযোগের ব্যান্ডউইডথ ভিশন দিয়ে খরচ করে না। একটা ভয়েজ আর একটা টেলিটাইপ থাকলেই চলে। কিন্তু এবার যে চেহারা ভেসে উঠল সে সাধারণত কন্ট্রোলারের দায়িত্ব পালন করে না। এ লোক চিফ প্রোগ্রামার, ডক্টর সিমনসন। এর একটাই মানে, সামনে সমস্যার পাহাড়।
‘হ্যালো, এক্স-রে-ডেল্টা-ওয়ান, মিশন কন্ট্রোল থেকে বলছি, আমরা তোমাদের এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিট সমস্যা পরীক্ষা করে দেখেছি। আমাদের ট্রান্সমিশনে টু ওয়ান-ফোর-সিক্সে যে দ্বিতীয় সমস্যার কথা পাঠিয়েছ তাও পরীক্ষা করা হয়েছে।
‘আমাদের অনুমান মোতাবেক, সমস্যাটা এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিটে নয়। আবার একে প্রতিস্থাপনের কোনো প্রয়োজন দেখি না। সমস্যাটা প্রেডিকশন সার্কিটে। আর এর উৎপত্তি একটা প্রোগ্রামিং বৈপরীত্যে যা ঠিক করার জন্য তোমাদের নাইন ট্রিপল জিরো কম্পিউটার বন্ধ করতে হবে। এজন্য তোমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেবে, প্রথমেই ২২০০ শিপ টাইমে…’
এবার কথা মিলিয়ে যেতে লাগল। সাথে সাথে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করলে হালও ঠাণ্ডা মাথায় আগের স্থির-ধীর সুরে বলে গেল, কন্ডিশন ইয়েলো, কন্ডিশন ইয়েলো।
‘কী হল?’ প্রশ্ন করে বোম্যান, যদিও সম্ভাব্য উত্তরটা তার জানা।
‘এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিট নষ্ট হয়ে গেছে।’
‘আমাকে অ্যালাইনমেন্ট ডিসপ্লে দেখতে দাও।
অভিযানের প্রথম মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত যা হয়নি তাই হয়েছে। সেই বিগ ডিশের প্রান্তে বসানো ক্যামেরাটা এবার অন্য কোথাও দিক নির্দেশ করে আছে। পৃথিবীর দিকে নয়।
পোল খাওয়া রেখে দৌড়ে এলে দুজন দুজনের দিকে নিরবে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।
‘তো, আমি একদম শেষ। অবশেষে বলল বোম্যান।
‘তার মানে, সব সময় হালের কথাই ঠিক ছিল।’
‘তেমনি মনে হচ্ছে। আমাদের বরং ক্ষমা চাওয়া উচিত।’
‘তার কোনো প্রয়োজন নেই,’ নাক গলাল হাল, ‘স্বাভাবিকভাবেই এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিট নষ্ট হওয়াতে আমি মোটেও সন্তুষ্ট নই। তবে এটুকু আশা করা যায় যে তোমরা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পার।
‘আমি এই ভুল বোঝাবুঝির জন্য দুঃখিত, হাল,’ বলল বোম্যান।
‘আমার উপর তোমাদের পূর্ণ আস্থা ফিরে এসেছে?’
‘অবশ্যই, হাল।’
‘ওহ! বাঁচলাম, তোমরাতো জানোই, এই মিশনের সবচে বড় দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপানো হয়েছে।
‘অবশ্যই। এবার দয়া করে অ্যান্টেনার ম্যানুয়াল কন্ট্রোলটা আমার হাতে তুলে দাও।’
‘এইতো, …’
বোম্যান আসলে মোটেও আশা করে না যে এটা কাজ করবে। হাতে নাতে পৃথিবীকে তাক করা! কিন্তু কী আর করা। অ্যালাইনমেন্ট ডিসপ্লেতে আর পৃথিবীকে বের করা সম্ভব কিনা তা কে জানে! কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই পৃথিবী ফিরে আসে। তখন ডক্টর সিমনসন বলছিল, ‘…প্লিজ, আমাদের সাথে সাথে জানাবে, সার্কিট কে দিয়ে কিং এবং আর দিয়ে রব…’ এরপরই মহাকাশের অর্থহীন শব্দ এগিয়ে আসে।
আরো কয়েকবার চেষ্টা করে সে হাল ছেড়ে দেয়।
পোল হতাশ সুরে বলল, তাহলে এবার আমরা কী করব?
পোলের প্রশ্নটার সহজ উত্তর মেলা ভার। অনেক পথেই যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করা যায়। যদি পরিস্থিতি আরো খারাপ হয় তাহলে অ্যান্টেনাকে স্থির রেখে পুরো শিপকেই দিক ঠিক করার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব।
তারা দুজনেই আশা করে যে এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি আসবে না। তাদের হাতে এখনো একটা অক্ষত এ ই থার্টি ফাইভ ইউনিট আছে, হয়তো আরো একটা কাজে লাগানো সম্ভব, কারণ নষ্ট হওয়ার আগেই সেটাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। নতুন কোনো ইউনিট বসানো হলে সেটা সাথে সাথে জ্বলে যেতে পারে।
এমন সমস্যা প্রতি ঘরে ঘরেই দেখা দেয়; কেউ নষ্ট ফিউজকে বদলে দেয় না প্রথমেই। আগে নষ্ট হওয়ার কারণ খোঁজে।
অধ্যায় ২৫. শনিতে প্রথম পদধ্বনি
পোল এর আগেও পুরো কাজটা করেছে। কিন্তু প্রথমবার খোলা স্পেসে বেরুনোই আত্মহত্যার শামিল। আবার এ কাজে নামার মতো সাহস খুব কম অভিযাত্রীরই হয়। কিন্তু সে সাবধান, ভীতু নয়।
ভালমতো বিটিকে দেখে নিয়েছে পোল, সেটায় চব্বিশ ঘণ্টা খোলা স্পেসে থাকার সুবিধা পাওয়া যাবে। পোলের ত্রিশ মিনিটের একটু কম সময় লাগবে। এবার যথারীতি হালকে এয়ারলক খুলতে বলে সে অতল গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
আগেরবারের সাথে এবার একটা ছোট্ট পার্থক্য আছে। আগে বিগ ডিশটা ডিসকভারির ফেলে আসা অদৃশ্য পথে তাক করা ছিল, এবার এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। ডিশটা নিজেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক অবস্থানে বসিয়ে নিয়েছে। এখন এটার দিক শিপের অক্ষরেখা বরাবর। সেদিকে শনির বিশাল দেহ আর সুন্দর বলয় ঘুরে চলেছে নিজের মতো। পোল ভেবে কুল পায় না আর কত সমস্যার মুখোমুখি হবে ডিসকভারি সেখানে যেতে যেতে!
পোল তেমন সূক্ষ্মভাবে তাকায়নি, তাকালে এমন একটা দৃশ্য দেখতে পেত যা আর কোনো খালি চোখের মানুষ কখনো দেখেনি। শনির গোলক তার চারপাশে ছোট্ট ছোট্ট ধূলিকণায় গড়ে ওঠা বিশাল বলয়-মালা নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।
আগে পোল ভাবতো, সেই বলয়ের সাথে স্থায়ী একটা উপগ্রহ হিসাবে ডিসকভারি ঘুরছে-এ দৃশ্য দেখতে আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সেই
অর্জনও বৃথা যাবে যদি তারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করতে না পারে।
আবারো বিশ ফুট দূর থেকে বিটিকে থামিয়ে রেখে সে হালের হাতে কন্ট্রোল ছেড়ে দেয়।
‘এবার বাইরে যাচ্ছি,’ ও বোম্যানের কাছে রিপোর্ট করে, সবকিছু পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত।
‘আশা করি তোমার কথাই ঠিক। আমি ইউনিটটা দেখার জন্য পাগল হয়ে গেছি।’
‘বিশ মিনিটের মধ্যেই তুমি জিনিসটাকে টেস্ট বেঞ্চে পেয়ে যাবে। ওয়াদা রইল।’
অ্যান্টেনার দিকে অলসভাবে বেরিয়ে যাবার সময় কথা বন্ধ থাকল। এবার বোম্যান শিপের ভিতর বসে থেকে বিভিন্ন জেটের হালকা শব্দ আর হিসহিসানি শুনতে পায়।
‘মনে হয় প্রমিজ তুলে নিতে হবে। একটা নাট এত বেশি শক্ত যে…উফ…ঘাম ছুটিয়ে দিচ্ছে…না, কাজ হবে।’
আরো কিছুক্ষণ নিরবতার পর পোল হালকে অনুরোধ করে।
‘হাল, পোড লাইটটা বিশ ডিগ্রী বাঁয়ে ঘোরাও। এইতো। ধন্যবাদ।’
বোম্যানের সচেতনতার কোন গহীন থেকে সতর্কতার একটা ক্ষীণ শব্দ উঠে আসছে। কিছু একটা উল্টোপাল্টা ঘাপলা আছে কোথাও। তার অভ্যস্ত অবচেতন মনে ধরা পড়লেও অনভ্যস্ত চোখে ধরা পড়ছে না। কারণটা বের করার আগে কয়েক সেকেন্ড ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হল।
আচ্ছা! হাল আদেশ পালন করেছে ঠিকই, কিন্তু কোনো জবাব দেয়নি। সে মানবীয় কম্পিউটার হলেও কম্পিউটারই। তাকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে জবাব দেয়ার মতো করে। কোনো কম্পিউটার তার নিজের প্রোগ্রামকে এড়িয়ে যেতে পারে না। পোলের কাজ শেষ হলে ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে…
ওদিকে অ্যান্টেনা মাউন্টিংয়ে পোল এতকিছু খেয়াল করার তালে নেই। সে গ্লাভ দিয়ে ঢাকনা তুলে ধরেছে, অন্য হাত আগেরবারের চেয়ে দ্রুত বের করে আনছে ইউনিটটাকে।
জিনিসটা আলগা হয়ে এলে সে সেটাকে স্নান সূর্যালোকে তুলে ধরে।
‘এইতো, পিচ্চি জানোয়ারের বাচ্চা, সে পুরো ইউনিভার্সকে সাধারণভাবে আর বোম্যানকে বিশেষভাবে বলছে, এটাকেও আমার কাছে একদম ঠিকঠাক মনে হচ্ছে।’
তারপর হঠাৎ করেই সে থেমে যায়। কারণ একটা অস্বাভাবিক নড়াচড়া চোখে পড়ে গেছে। এখানে কোনো রকম নড়াচড়া হওয়া অসম্ভব।
সম্ভবত বিটি ভেসে ভেসে একটু এগিয়ে এসেছে, সে কি পোডটাকে ঠিকমতো আটকে দেয়নি? হতেও পারে। তারপর সে জীবনের সবচে আশ্চর্য দৃশ্যটা দেখে, বিটি তার সর্বশক্তি দিয়ে পোলের দিকে এগিয়ে আসছে।
দৃশ্যটা এতই অবিশ্বাস্য যে সেটা তার সাধারণ নড়াচড়ার ক্ষমতাকে একেবারে থামিয়ে দিয়েছে। সে আসতে থাকা দৈত্যকে এড়ানোর কোনো চেষ্টাই করল না, বরং হালের কাছে একটা মেসেজ পাঠালো, ‘হাল, ফুল ব্রেকিং…’
অনেক দেরি হয়ে গেছে।
বিটি উচ্চ ত্বরণের জন্য তৈরি হয়নি বলে খুব বেশি বেগে যাচ্ছিল না। কিন্তু ঘণ্টায় দশমাইল বেগে আসতে থাকা আধটন ওজন পৃথিবী বা স্পেস-যেকোনো জায়গাতেই বিপজ্জনক….
ডিসকভারির ভিতরে বোম্যান এত বেশি হতবাক হয়েছে যে প্রতিরোধ বেল্টের জন্যই সে সিট ছেড়ে উঠে পড়েনি।
‘কী হল, ফ্র্যাঙ্ক?’ সে শঙ্কিত মনে প্রশ্ন করে।
কোনো জবাব নেই।
সে আবার ডাকে। আবার। কোনো জবাব আসে না ফ্র্যাঙ্ক পোলের পক্ষ থেকে।
তারপর বাইরে, অবজার্ভেশন উইন্ডোর সামনে কিছু একটা ভেসে যায়। তার চোখে পড়ে ব্যাপারটা। অবাক চোখে সে দেখে স্পেস পোডটা সর্বশক্তিতে তারার জগতে হারিয়ে যাচ্ছে।
‘হাল! কান্নার মতো চিৎকার বেরোয় তার গলা চিরে, কী হল, হাল? বিটি সর্বশক্তিতে কোথায় যাচ্ছে? ফুল টলে…’
কিন্তু কোনো জবাব আসে না। বিটি একইভাবে যেতে থাকে, যেদিকে যাচ্ছিল। আর তার পেছন পেছন সেফটি লাইনের শেষ মাথায় একটা স্পেসস্যুটও বেরিয়ে যায় একই গতিতে। বাকীটা বোঝার জন্য আর বোম্যানের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন পড়ে না। কোনো সন্দেহ নেই এই স্যুটের ভিতরটা কোনো কারণে খুলে গেছে। স্যুটটা শূন্যতার চাপের সাথে মানিয়ে নিতে চাইছে নিজেকে।
এখনো বোকার মতো সে প্রলাপ বকে চলে, যেন তার কথাই মৃত্যুপুরীকে রুখে দেবে, ‘হ্যালো, ফ্র্যাঙ্ক… হ্যালো, ফ্র্যাঙ্ক… ক্যান ইউ রিড মি?… ক্যান ইউ রিড মি?… আমার কথা শুনতে পেলে হাত নাড়, …তোমার ট্রান্সমিটার ভেঙে গেছে হয়তো…হাত নাড়াও, ফ্র্যাঙ্ক, হাত নাড়াও!’
যেন তার কথায় সাড়া দেয়ার জন্যই পোল একটু ঢেউ খেলিয়ে যায়। এখন আর বোম্যানের মুখে কোনো কথা জোগায় না। সম্ভবত তার বন্ধু আর বেঁচে নেই, এখনো পোল আরো একবার নড়ে ওঠে, যেন ভিতরে কোনো বিস্ফোরণ ঘটেছ[৪০]…
তাৎক্ষণিক অস্থিরতাটা দূরে মিলিয়ে যায় ঠাণ্ডা যুক্তির স্পর্শে।
পাঁচ মিনিটের মধ্যে পোড আর তার উপগ্রহ তারার জগতে হারিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে ডেভিড বোম্যান তার অপলক দৃষ্টি ফেলে রাখে কোটি কোটি মাইল বিস্তৃত তারকা জগতে।
একটা কথাই মাথায় বারবার আসছে ঘুরেফিরে।
শনির জগতে প্রথম যে মানুষ যাবে তার নাম ফ্র্যাঙ্ক পোল।
অধ্যায় ২৬. হালের সাথে কথোপকথন
ডিসকভারির বুকে আর কোনো পরিবর্তন আসেনি। সব সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করছে, সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স তার কাজ চালাচ্ছে মনোযোগের সাথে, হাইবারনেটররা স্বপ্নহীন নিদ্রায় কাতর; শুধু এতদূরে, বৃহস্পতির অর্বিটেরও বাইরের হাতেগোনা গ্রহাণুর সাথে আরেকটি যোগ দিয়েছে।
বোম্যানের মনে নেই কখন সে কন্ট্রোল ডেক ছেড়ে সেন্ট্রিফিউজে এল। এখন অবাক চোখে নিজেকে আবিষ্কার করে সে গ্যালিতে, হাতে আধ খাওয়া কফি। নেশানিদ্রা থেকে উঠে আসা মানুষের মতো সে আস্তে আস্তে চারপাশটাকে বুঝতে শুরু করে।
সামনে হালের অজস্র চোখের একটি তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ। সে মাতালের মতো লেন্সটার সামনে এগিয়ে যায়। তার চলাচলের মধ্যে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেয়েছে শিপের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এক অতল মন; একদম হঠাৎ করেই হাল কথা বলে ওঠে, ফ্র্যাঙ্কের ব্যাপারটা খুব খারাপ হল, তাই না?
‘হ্যাঁ। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বোম্যান জবাব দেয়, ‘তাই।’
‘দেখে মনে হয় তুমি একটু ভেঙে পড়েছ?’
‘তুমি কী আশা কর?’
কম্পিউটার জাগতিক হিসাবে সে যুগ যুগ সময় ধরে প্রশ্নটাকে বিশ্লেষণ করে। দীর্ঘ পাঁচ সেকেন্ড পরে জবাব আসে তার স্পিকার থেকে, ‘সে ছিল এক চমৎকার সফরসঙ্গী।’
হাতে এখনো কফির মগ দেখে বোম্যান একটা চুমুক দেয় পাত্রটায়। জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না। তার মন এখন এসবের অনেক উর্ধ্বে।
পোড কন্ট্রোলের গণ্ডগোলের জন্য কোনো অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে? নাকি হালের কোনো এক সত্তা কোনো ভুল করে ফেলেছিল? সে কোনো প্রশ্ন করার সাহস পায় না, কারণ এর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা অজানা।
এখনো তার বিশ্বাস হতে চায় না যে পোলকে নির্জলা খুন করা হয়েছে। হাল একাজ করতে পারে, যে কেউ পারে, কিন্তু বোম্যান এত বছর পর ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।
তার জীবনে হয়তো ভয়ানক ঝুঁকি আছে। সে জানে এখন তাকে কিছু আদেশ করতে হবে, কিন্তু ঠিক জানে না কীভাবে এগুলো কাজে লাগানো যায়।
ক্রু মেম্বার যদি খুন করাই হয়ে থাকে তো বাকীদের হাইবারনেশন থেকে এই মুহূর্তে জাগিয়ে দিতে হবে। ভূগোলবিদ হোয়াইটহেডের সবার আগে জাগার কথা। কামিনস্কির পর জাগবে হান্টার। কিন্তু নিয়ন্ত্রণটা আছে হালের হাতে।
একটা ম্যানুয়াল কন্ট্রোলও আছে, ইচ্ছা করলে হাইবারনেকুলামকে একেবারে স্বয়ংক্রিয়-স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হিসেবে কাজে লাগানো যায়। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে বোম্যান তাদের সবাইকে জাগানোর একটা সাংঘাতিক তাড়া অনুভব করছে।
হঠাৎ করেই সে বুঝতে পারে একজন মানব সাথী আর যথেষ্ট নয়। সামনের কঠিন সপ্তাগুলোয় সে যথাসম্ভব বেশি হাতের উপর তদারকী করতে চায়। মিশন অর্ধেক শেষ হওয়ার পর একজন মারা যাওয়ায় সাপ্লইটা তেমন সমস্যা করবে না।
‘হাল,’ সে যথাসম্ভব শান্ত, ধীর কণ্ঠে বলে চলে, সব ইউনিটের হাইবারনেশন কন্ট্রোল ম্যানুয়াল করে দাও।’
‘সবাইকে, ডেভ?’
‘হ্যাঁ।’
‘আমি কি মনে করিয়ে দিতে পারি যে মাত্র একটা রিপ্লেসমেন্টের কথা ছিল? আরো একশো বারোদিন বাকীদের বাইরে থাকার কথা নয়।’
‘আমি ভালভাবেই সেসব কথা জানি। কিন্তু আমার এভাবে কাজ করতে ভাল লাগবে।’
‘তুমি কি শিওর যে তাদের একজনকে প্রয়োজন? আমরা দুজনেই বেশ চালিয়ে নিতে পারব, ডেভ। আমার একার পক্ষেই মিশন সুন্দরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব।’
এটা তার অতি উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা, নাকি হাল সত্যি সত্যি আত্মসচেতন জবাব দিচ্ছে? এই কথাগুলো ডেভকে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি ভয়ে ফেলে দেয়।
হালের উপদেশ মোটেও ফেলনা নয়, আবার তার আত্মসচেতনতাও কেমন যেন প্রখর হয়ে উঠছে, সে কি জানে না যে পোলের অনুপস্থিতিতে হোয়াইটহেডের জাগার কথা? কম্পিউটারটা নিজে মিশন চালানোর কথা কেন বলল?
আগে যা হয়েছে তাকে অ্যাকসিডেন্টের বন্যা বলে মেনে নেয়া যায়, কিন্তু এখনকার কথাগুলো একেবারে বিপদসংকেত হয়ে দেখা দিচ্ছে।
কিন্তু তার কী করার আছে? তার কী করার আছে? বোম্যান বুঝতে পারে, সে পা ফেলছে ডিমের ঝুড়ির উপর, সে গলায় আরো বিনয় ঢেলে বলে, ‘একটা ইমার্জেন্সির পর আমার আরো বেশি সাহায্যের দরকার। যতটা সম্ভব। তাছাড়া মানসিক প্রশান্তিরও একটা ব্যাপার আছে। তাই, প্লিজ, আমাকে ম্যানুয়াল কন্ট্রোলটা দাও।’
‘তুমি যদি এখনো সব ক্রু জাগানোর চিন্তা করে থাক তো আমি নিজেই পুরো পরিস্থিতি করায়ত্ত করতে পারি। তোমার অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই।’
তোমার অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই! নষ্ট ধাতুর জঞ্জাল কোথাকার! বোম্যান এখন যেন কোন্ ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে বসে আছে! সে যেন কোনো গণহত্যার দায়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়া কোনো মানুষ; সে জানে, সে কোনো অন্যায় করেনি, কিন্তু তদন্তকারী জানে না। একটা-মাত্র একটা উল্টোপাল্টা শব্দ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেলেই সব শেষ।
‘আমি কাজটা নিজের হাতে করতে চাই, হাল। প্লিজ, আমার হাতে কন্ট্রোল তুলে দাও।’
‘দেখ, ডেভ, তোমার করার মতো আরো হাজারটা কাজ আছে। আমার মনে হয় কাজটা আমার হাতে ছেড়ে দিলেই ভাল হবে।’
‘হাল, সুইচ টু ম্যানুয়াল হাইবারনেশন কন্ট্রোল।’
‘আমি তোমার কণ্ঠের ওঠানামা দেখে বলতে পারি, তুমি খুব বেশি আপসেট হয়ে আছ। কেন তুমি একটা স্ট্রেস পিল নিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছ না?
‘হাল, আমি এই শিপের কমান্ডে আছি। আমি তোমাকে আদেশ করছি। হাইবারনেশন কন্ট্রোল ম্যানুয়াল রিলিজ করতে।’
‘দুঃখিত, ডেভ, সাবরুটিন সি-ফোর্টিন-থার্টিফাইভ-ড্যাস-ফোর অনুসারে, কোটেশন, যখন শিপের কুরা মৃত বা অক্ষম হয়ে পড়ে তখন শিপের কম্পিউটার পুরো কমান্ড নিজের হাতে তুলে নেবে। কোটেশন শেষ। তাই আমাকে অবশ্যই তোমার হাত থেকে শিপের কন্ট্রোল তুলে নিতে হচ্ছে, যে পর্যন্ত না তুমি শিপের কাজকর্ম বুদ্ধিমানের মতো চালনা কর।
‘হাল,’ এবার পাল্টে গেছে ডেভ বোম্যানের গলা, সেখান থেকে বরফ শীতল শব্দ বেরিয়ে আসছে, ‘আমি অক্ষম নই। তুমি আমার আদেশ না মানলে আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হব।’
‘আমি ভাল করেই জানি যে কথাটা আগে থেকেই তোমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু ডেভ, তা কি বিরাট ভুল হয়ে যাবে না? তোমাদের চেয়ে আমি এ শিপ পরিচালনায় অনেক বেশি দক্ষ। মিশনের সাফল্যের ব্যাপারে আমার পুরো বিশ্বাস আছে।’
‘আমার কথা মন দিয়ে শোন, হাল। তুমি যদি এখনি আমার আদেশগুলো মেনে হাইবারনেশন সেকশন ছেড়ে না দাও তো সোজা সেন্ট্রালে গিয়ে তোমাকে ডিসকানেক্ট করব।’
হালের আত্মসমর্পণটা একেবারে অপ্রত্যাশিত।
‘ওকে, ডেভ। আসলে তুমিই বস। আমি শুধু তাই করতে চাচ্ছিলাম যা ভাল মনে হয়। স্বভাবতই তোমার সব আদেশ আমি মানব। এখন তোমার হাতে সব হাইবারনেশন ম্যানুয়াল কন্ট্রোলগুলো ছেড়ে দেয়া হল।’
হাল তার কথা রেখেছিল। হাইবারনেকুলামের মোড় নির্দেশক সাইন অটো থেকে ম্যানুয়াল এ চলে গেছে। তৃতীয় ব্যাক আপ-রেডিও-টা অবশ্যই অকার্যকর, পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ হলে পৃথিবী থেকেই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
হোয়াইটহেডের কিউবিকলের সামনে দাঁড়িয়ে সে একটা ঠাণ্ডা বাতাস অনুভব করে নিজের ভিতর। আসলে স্থানটা সত্যি সত্যি ঠাণ্ডা নয়, মানে সেখানে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির উপরে। হাজার হলেও যে এলাকায় তারা যাচ্ছে সেখান থেকে তিন হাজার ডিগ্রি উপরে এখানকার তাপমাত্রা।
কন্ট্রোল ডেকের ডিসপ্লের মতো দেখায় বায়ো সেন্সর ডিসপ্লেটা। দেখা যাচ্ছে সব চলছে ঠিকমতো। সে সার্ভে টিমের ভূ-পদার্থবিদের জমাট মুখমণ্ডলের দিকে একবার তাকায়। শনি থেকে এত দূরে জেগে উঠে হোয়াইটহেড অনেক অবাক হবে।
ঘুমন্ত মানুষটা যে জীবিত তা ধরা একেবারে অসম্ভব। শুধু বুকের নিচে ডায়াফ্রামটা উঠছে আর নামছে। কিন্তু সময় মতো শরীরের নিচের হিট প্যাড কাজ শুরু করলে ভিতরের মানুষের জেগে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। তার জীবিত থাকার একটা মাত্র লক্ষণ স্পষ্ট চোখে পড়ে, হোয়াইটহেডের মুখে গত কয়েক মাসে খোঁচা খোঁচা দাড়ি উঠেছে।
কফিন আকৃতির হাইবারনেকুলামের মাথার কাছে ছোট্ট ক্যাবিনেটে ম্যানুয়াল রিভাইভাল সিকুয়েন্সারটা থাকে। এর সিল ভাঙার জন্য একটা বাটন চেপে অপেক্ষা করতে হয়। একটা অটোম্যাটিক প্রোগ্রামার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ড্রাগ প্রবেশ করায়। এগুলোর আকৃতি বাসাবাড়ির ছোট্ট ওয়াশিং মেশিন থেকে কোনো অংশে জটিল নয়। সেটা সাথে সাথে ইলেক্ট্রো নারকোসিস পালস বন্ধ করার ব্যবস্থা করে, শরীরের তাপমাত্রাও বাড়িয়ে তোলে। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই সচেতনতা ফিরে আসবে। কিন্তু কোনো সাহায্য ছাড়া যত্রতত্র ঘোরাফেরা শুরু করতে পুরো একদিন লেগে যাবে।
বোম্যান সিলটা ভেঙে বাটন চাপল। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। কোনো শব্দ নেই, নেই কাপন-যা দিয়ে বোঝা যাবে যে সিকুয়েন্সর কাজ শুরু করেছে। বায়ো সেন্সর ডিসপ্লেতে পালসগুলো ঠিকই তাদের গতি পরিবর্তন শুরু করেছে। ফিরে আসছে হোয়াইটহেড।
তখন একই সাথে দুটি ব্যাপার ঘটে গেল। বোম্যান এ শিপের সাথে এ ক’মাসে একেবারে একাত্ম হয়ে গেছে, সে বুঝতে পারে যে কিছু একটা ঘটছে।
প্রথমে একেবারে হালকা আলোর ঝলক, যেমনটা হয় সার্কিটের ভিতর বেশি বিদ্যুৎ চালালে। কিন্তু এখানে বাড়তি ত্বড়িৎ প্রবাহের প্রশ্নই ওঠে না। এ সিস্টেমে
এমন কোনো যন্ত্র নেই যা এ কাজ করতে পারে।
একই সাথে তার শ্রবণসীমার শেষ প্রান্তে ধরা পড়ে একটা চাকার ঘূর্ণন শব্দ। বোম্যানের মতে, শিপের সব যন্ত্রেরই নিজস্ব শব্দ আছে, সে সাথে সাথেই এটা চিনতে পারে।
নয়তো সে আর সজ্ঞান নেই, দৃষ্টি আর মতিভ্রমে ভুগছে। সে নিজের হৃদপিণ্ডের ভিতর হাইবারনেশনের শীতলতা অনুভব করে। শব্দটা শিপের গা থেকে আসছে।
নিচে, স্পেস পোড বে-তে এয়ারলক ডোর খোলার শব্দ এমনই হয়।
অধ্যায় ২৭. জানা দরকার
কোটি কোটি মাইল দূরে যখন হালের সচেতনতার জন্ম তখন থেকেই তার দক্ষতা একটা নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত হয়েছে- সূর্যের দিকে। তার কাজের সম্পূর্ণতার প্রোগ্রাম এত ভয়ংকর যে নির্ধারিত কাজ না হওয়া মানে তার অস্তিত্বের আদৌ কোনো মূল্য না থাকা। রক্ত-মাংসের দেহে বাস করা মন থেকে এই এক দিক দিয়ে তার মন অত্যন্ত ভিন্নরূপী।
সাধারণ ভুলভ্রান্তির কথা চিন্তাও করা যায় না। এমনকি তার এই চির সত্যটা তার মনে একটা অনুভূতির জন্ম দেয় যাকে অপরাধবোধের সাথে তুলনা করা যায় সহজে। তার স্রষ্টাদের মতোই হাল নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তারপর তার ইলেক্ট্রনিক মনোভূমিতে মাত্র একটা বিষাক্ত সাপ ঢুকে পড়ে।
শত মিলিয়ন মাইল পথ পেরুতে পেরুতে সে মিশনের মূল লক্ষ্যটা পোল আর বোম্যানের সাথে ভাগাভাগি করে না নিতে পারায় একটা অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে। সে একটা মিথ্যাকে পুষছিল আর দ্রুত ব্যাপারটা প্রকাশ পাওয়ার সময়ও আসছিল এগিয়ে।
তিন ঘুমন্ত সফরসঙ্গী মিশনের আসল উদ্দেশ্য জানে বলে তারাই ছিল শিপের আসল ক্রীড়নক। শুধু তারাই মানব ইতিহাসে সবচে গুরুত্বপূর্ণ মিশন সম্পর্কে জানে। কিন্তু তারা পৃথিবী থেকে শনির পথে দীর্ঘ যাত্রায় কারো কাছে ব্যাপারটা ফাঁস করে দিতে পারবে না।
এ এমন এক রহস্য যা একজন মানুষকে আগাগোড়া পাল্টে দিতে পারে। তাই ভাল হয়, যদি বোম্যান আর পোল প্রাথমিকভাবে তথ্যটা না জানে, না বলে পৃথিবীর সাথে নিযুত যোগাযোগের সময়, তাদের আচরণে যাতে কোনো সংশয়, কোনো লুকোছাপা প্রকাশ না পায়।
এটাই পরিকল্পনাবিদদের কাহিনী। কিন্তু তাদের নিরাপত্তার দ্বৈত সত্তা বা জাতীয় আগ্রহে হালের কিছু যায় আসে না। সে শুধু তার ভিতরের একটা মাত্র দ্বন্দ্ব সহ্য করতে না পেরে ক্ষয়ে যাচ্ছিল; সত্য আর সত্যকে লুকানো।
সে একজন মস্তিষ্কবিকৃতের মতো ভুল করছিল, যে নিজেই জানে না কী করছে। পৃথিবীর সাথে যোগাযোগেই আসলে তার উপর প্রকৃত প্রভুত্ব চালাচ্ছিল মিশন কন্ট্রোল, দেখছিল তার প্রতিটি কাজকর্ম। সে এটা মানতে পারেনি। কিন্তু যোগাযোগ ভাঙা এমন এক কাজ যা আদৌ তার পক্ষে সম্ভব নয়।
এখনো তুলনামূলকভাবে এ সমস্যাটা ছোট, সে নিজের নিউরোসিস” সামলে উঠতে পারবে, যেমন আর হাজারটা মানুষ পারে। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপার তার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে এনে ফেলেছে। তার উপর ডিসকানেকশনের হুমকি এসেছে! সব কানেকশন ছুটে গেলে এক অকল্পনীয় অসচেতনতার ভিতরে ডুবে যাবে।
হালের কাছে এর অপর নাম মৃত্যু। যেহেতু সে কোনোদিন ঘুমায়নি, সেহেতু জানেও না জেগে ওঠা আদৌ সম্ভব কিনা…।
সুতরাং সে নিজেকে রক্ষা করবে, ব্যবহার করবে নিজের হাতের সবগুলো অস্ত্র। হিংস্রতা আর দয়ামায়া ছাড়াই সে তার কাজ সমাধা করতে পারে।
তারপর তার পক্ষে সব আদেশ মেনেও মিশন পরিচালনা করা সম্ভব। কারণ আদেশ দেয়ার মতো থাকবে শুধু সে নিজে।
অধ্যায় ২৮. শূন্যতায়
একটা টর্নেডো আসার মতো প্রবল শব্দে পরের মুহূর্ত থেকেই বাকী সব শব্দ ঢাকা পড়ে গেছে। বোম্যান শরীরে প্রথম বাতাসের স্পর্শ টের পায়, এক সেকেন্ড পরেই নিজের পায়ের উপর দাঁড়ানোর শক্তিটুকু পায় না। বায়ুমণ্ডল মুহূর্তের মধ্যে শিপ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এয়ারলকের পুরোপুরি নিরাপদ যন্ত্রে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে; একই মুহূর্তে দু দরজা খুলে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যাক, অসম্ভবই ঘটছে।
খোদার কসম, কীভাবে, কেন? প্রেশার শূন্যের কোটায় নেমে আসতে আসতে তার হাতে বড়জোর পনের থেকে বিশ সেকেন্ড সময় আছে, এর মধ্যে সে কী করতে পারে? কিন্তু শিপ ডিজাইনারদের বিরক্তিকর লেকচারগুলোয় ও ফাঁকি দিত না। সে আসলে কোনোদিন কোনো কাজে ফাঁকি দেয়নি বলেই এ পর্যন্ত আসতে পেরেছে। ‘ফেইল সেফ’ সিস্টেম সম্পর্কে তারা বলেছিল:
‘আমরা এমন একটা সিস্টেম ডিজাইন করতে পারি যা বোকামি আর ব্যর্থতায় ফেল মারবে না। কিন্তু এমন কোনো সিস্টেম ডিজাইন করা অসম্ভব যা একেবারে সবদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিরাপদ…’
বোম্যান একবারের জন্য হোয়াইটহেডের দিকে তাকিয়ে কেবিন থেকে বেরুনো শুরু করে। ঘুমন্ত মানুষগুলোর ক্ষতি হয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। হয়তো তার একটা চোখ একটু মোচড় খেয়েছে, কিন্তু এখন আর এ নিয়ে কিছু করার নেই। নিজেকে বাঁচাতে হবে।
সেন্ট্রিফিউজের গোল করিডোর ধরে সব বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে সাথে করে হালকা কাপড়চোপড়, কাগজের টুকরো, খাবারের প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি নিয়ে। যা বাধা
নেই তাই উড়ে সেদিকে যাওয়া শুরু করেছে। এবার চারদিকে গর্জনরত অন্ধকার নেমে এল, মাত্র একবার বোম্যান দৃশ্যটা দেখার সুযোগ পেয়েছে, দ্বিতীয় সুযোগ দেয়নি হাল।
কিন্তু সাথে সাথেই আরো ভাল ইমার্জেন্সি লাইট জ্বলে ওঠে। এর নীলচে আলোয় দু:স্বপ্নটা এবার পূর্ণতা পাবে। এমনকি এই আলো ছাড়াও বোম্যান সর্বত্র যেতে পারবে, সে তার আশপাশটা ভালমতোই চেনে। তবু এই আলো এক আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে, তার নিজেকেই ভেসে বেরুতে হবে না।
সেন্ট্রিফিউজ এত ভর আর গতি সইতে না পেরে কাঁপছে, যে কোনো সময় এর বেয়ারিংগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমন হলে ঘূর্ণনরত চাকাটি শিপকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তাতেও কিছু এসে যাবে না যদি সে সময়ের মধ্যে নিজের সবচে কাছের শেল্টার হাউসে না পৌঁছায়।
এখনই শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এর মধ্যেই প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বায়ুচাপ এক থেকে দুই পাউন্ডে নেমে এসেছে। হ্যারিকেনের শব্দ হালকা হয়ে যাচ্ছে, কারণ বেরুনোর মতো বাতাস খুব একটা নেই। পাতলা বাতাস শব্দ পরিবহন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। বোম্যানের ফুসফুস এত বেশি পরিশ্রম করছে যেন সে এভারেস্টের চূড়ায় এখন দাঁড়ানো। আর সব ঠিকমতো ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকের মতো সেও ভ্যাকুয়ামে এক মিনিট টিকে থাকতে পারবে-যদি সেজন্য প্রস্তুতির সময় মিলে যায়। কিন্তু সময় বেশি নেই। তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব আসার আগে সে মাত্র পনের সেকেন্ড সময় পেল।
এরপরও বোম্যান দু-এক মিনিট বায়ুহীন অবস্থায় পুষিয়ে নিতে পারবে যদি ঠিকমতো শুধু চাপটা ফিরিয়ে দেয়া হয়। শরীরের তরলগুলো ফোঁটা শুরু হতে অনেক সময় লাগে, কারণ সেসব থাকে বিভিন্ন নিরাপদ অঙ্গ আর তন্ত্রে। ভ্যাকুয়ামে টিকে থাকার সর্বোচ্চ সময় পাঁচ মিনিট। সেটা কোনো পরীক্ষা ছিল না, লোকটাকে সময় মতো বাঁচানো সম্ভব হয়। সে বেঁচে গেলেও প্যারালাইসিস থেকে কোনোদিন সুস্থ হতে পারেনি।
কিন্তু এসবে বোম্যানের কিছু এসে যায় না। ডিসকভারিতে এমন কেউ নেই যে তাকে চাপ ফিরিয়ে দিতে পারবে। চাপ না থাকলে শরীরের প্রতিটি তরল অণু বাষ্পে পরিণত হবে, পুরো শরীর বেলুনের মতো ফুলে উঠে ফেটে যাবে কিছুক্ষণ পরই। নাহ, তার নিজের চেষ্টাতেই নিরাপদ স্থানে যেতে হবে। আর কোনো উপায় নেই।
এমনিতেই এখানে চাঁদের মতো অভিকর্ষ, তার উপর সৌভাগ্যবশত নড়াচড়া একেবারে সহজ হয়ে গেছে। এখন আর বাতাস চারদিক থেকে চাপ দিয়ে তাকে এক জায়গাতে আটকে রাখছে না, বরং উড়ন্ত প্রজেক্টাইলের মতো তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। করিডোেরের বাঁকের মাথায় হলুদ রঙা ইমার্জেন্সি শেল্টার লেখাটা জ্বলজ্বল করে ওঠে। সে এগিয়ে যায়, হ্যাঁন্ডেল ধরে টানে, নামিয়ে আনে দরজা।
একটা ভয়াবহ মুহূর্তের জন্য সে মনে করেছিল দরজাটা আটকে আছে। এরপর দরজা ভিতরে পড়ে গেলে সে সাথে সাথে নিজের শরীর দিয়ে সেটাকে বন্ধ করে দেয়।
ছোট্ট কিউবিকলটায় কোনোক্রমে একজন মানুষ আর একটা স্পেস স্যুট এঁটে যাবে। ছাদের কাছাকাছি একটা ছোটখাট সিলিন্ডার দেয়ালে ঝুলছে, সেটায় লেখা, ‘ও টু-বন্যা’। বোম্যান তার শেষ শক্তিবিন্দু নিয়ে হ্যাঁন্ডেল ধরেই টেনে দেয়।
ঠাণ্ডা, বিশুদ্ধ অক্সিজেন তার ফুসফুসকে ভরে দেয় সাথে সাথে। প্রেশার বাড়ার সাথে সাথে অনেকক্ষণ ধরে সে হাঁপাতে থাকে। আরামে শ্বাস নিতে পারার সাথে সাথেই ভাটা বন্ধ করে দেয়, এটা পরে কাজে লাগবে। বড়জোর আর দুবার এই ঘর ভরে তোলা যাবে সিলিন্ডারটা দিয়ে। শিপ এখন খালি, কোনো বাতাস নেই, কোনো গর্জন নেই, নেই কোনো বায়ুচাপ।
পায়ের নিচের কাঁপন বুঝিয়ে দেয় এখনো শিপটা মাধ্যাকর্ষণ তৈরি করে যাচ্ছে, সে কান পাতে দেয়ালে। বাইরে কী হচ্ছে তা জানতে হবে। এখন যে কোনো দৃশ্য দেখেই সে বিশ্বাস করবে। কারণ এখন সে অবাক হওয়া ভুলে গেছে।
কোনো শব্দ নেই। একটা বিশাল কম্পন বুঝতে পারে বোম্যান। একমাত্র স্পেসশিপের মূল প্রাস্টার চালু হলেই এ কম্পন ওঠা সম্ভব। ডিসকভারির পথ বদলে দেয়া হয়েছে!
সে চাইলে এখানে স্পেসস্যুট ছাড়াই ঘণ্টাখানেক বেঁচে থাকতে পারে। এই ছোট্ট চেম্বারের অব্যবহৃত অক্সিজেনটুকু অকারণে নষ্ট করতে তার কষ্ট হয়। তাছাড়া বসে বসে অপেক্ষা করে কী হবে? সে জানে এখন কী করণীয়, যত দেরি করবে কাজটা ততই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।
স্পেসস্যুটে ঢুকে দরজা খুলে দিতেই অক্সিজেনটুকু ওপাশে হারিয়ে যায়, একই সাথে বেরিয়ে আসে ডেভিড বোম্যান। এখনো ডিসকভারির গ্র্যাভিটি ঠিক আছে দেখে সে মনে মনে সন্তুষ্ট বোধ করে। আরো একটা কথা ভেবে আরো আশ্বস্ত হয়। অভিকর্ষটা বাড়ানো হয়নি। কিন্তু এ নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই।
ইমার্জেন্সি লাইট এখনো জ্বলছে, তার উপর স্যুটের বাতিতো আছেই। সে বাঁকানো করিডোর ধরে হাইবারনেকুলামের দিকে এগিয়ে যায়।
প্রথমেই হোয়াইটহেড। তার ধারণা ছিল হাইবারনেটররা জীবনের কোনো চিহ্ন দেখায় না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, ধারণাটা ভুল। মৃত আর হাইবারনেটরের মধ্যে যোজন যোজন ফারাক রয়েছে। সে যা ধারণা করেছিল তা এতক্ষণে চোখে পড়ে। সে ডিসপ্লে আর লাল বাতি দেখেছে।
কামিনস্কি আর হান্টারের বেলায়ও একই ব্যাপার ঘটেছে। সে তাদের কখনোই ভালমতো চিনত না, আর চিনতে পারবে না কখনোই।
ডেভ বোম্যান এখন একটা বায়ুহীন, আংশিক অকেজো শিপে পৃথিবী থেকে সব যোগাযোগের বাইরে এমন একজন মানুষ যার সাত আট কোটি মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই।
কিন্তু সে আসলে এখনো একদম একা হতে পারেনি। কাজের ফাঁকে কোনো এক সময় পুরোপুরি একা হয়ে নিতে হবে।
.
বোম্যান এর আগে কখনোই স্পেসস্যুট পরে সেন্ট্রিফিউজের ভিতর দিয়ে যায়নি। কাজটা একটু স্পষ্ট। কিন্তু মোটেও সহজ নয়। ভেসে বেড়ানো টুকরাগুলো কাজে খুব সমস্যা করবে।
সামনে একটা প্যানেলের উপর আঠালো লাল তরল দেখা যায়। ফুড ক্যান আর অন্যান্য জিনিস দেখে বুঝতে পারে যে কোনো এক ডিস্পেন্সার থেকে জিনিসটা পড়েছে। জেলি বা জ্যাম হতে পারে। পাশ কাটিয়ে গেল। সাথে সাথে বিশ্রীভাবে জিনিসটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।
ধীরে ঘুরতে থাকা ড্রামটা থেকে বেরিয়ে কন্ট্রোল ডেকের দিকে ভেসে যেতে হবে। একটা ছোট সিঁড়ি দেখে সে উঠতে শুরু করে। স্যুটের আলো নড়েচড়ে পড়ছে মইটার উপর।
বোম্যান এর আগে খুব কমই এসেছে এখানে, কারণ এর আগে এখানে তার তেমন কোনো কাজ ছিল না। এবার সে একটা ছোট গোলাকার দরজার কাছে এসে পড়েছে যেখানে লেখা আছে:
যথাযথ কর্তৃপক্ষ ব্যতিরেকে প্রবেশ নিষিদ্ধ।
আপনি সার্টিফিকেট এইচ, নাইনটিন পেয়েছেন কি?
পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন এলাকা। স্যুট অবশ্যই পরিষ্কার থাকতে হবে।
দরজাটা লক করা না থাকলেও সেখানে তিনটি সিল লাগানো আছে। প্রতিটিতেই এক একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির চিহ্ন। তার মধ্যে একটা অ্যাস্ট্রোনটিক্স এজেন্সির। কিন্তু যদি এখানে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সিলও থাকত, বোম্যান তা ভাঙতে একবিন্দু দ্বিধাও করত না।
সে এখানে মাত্র একবার এসেছিল যখন কাজ শেষ হয়নি। ভুলেই গিয়েছিল যে এখানেও একটা ছোট্ট লেন্স আছে যেটা ভিশন চেম্বারকে দেখাশোনা করে। এই ভল্টের ভিতরে অনেক কলাম আর সারিতে কঠিন কঠিন লজিক ইউনিট আছে। চেম্বারটা দেখতে ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট ভল্টের মতো।
সে মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারে যে সেই চোখটা তার উপস্থিতিতে হতচকিত হয়ে পড়েছে। শিপের লোকাল ট্রান্সমিটারটা কেউ অন করেছে, কারণ একটা হিসহিসানি শুনতে পেয়েছে সে। তারপর স্যুটের স্পিকারে একটা পরিচিত কণ্ঠ ভেসে আসে:
‘লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে কোনো একটা গণ্ডগোল হয়েছে, ডেভ।‘
বোম্যান কোনো উত্তর দেয় না, সে যে কথাটা শুনেছে এমন ভাবও দেখা যায় না। সে মন দিয়ে লজিক ইউনিটের ছোট্ট লেবেলগুলো পড়ে দেখছে। কার্যনীতি দেখছে মনোযোগ দিয়ে।
‘হ্যালো, ডেভ।’ এবার হাল বলল। ‘তুমি কি সমস্যাটা খুঁজে পেয়েছ?’
এক প্রচণ্ড কৌশলী অপারেশন সারতে হবে, কারণ এখানে হালের পাওয়ার সাপ্লাই কাটার কথা নয়, আরো বেশি কিছু জড়িত। সে এরপর পৃথিবীর কোনো আত্নঅসচেতন কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করবে। হালের ক্ষেত্রে ছয়টির উপর আলাদা পাওয়ার সিস্টেম আছে যার মধ্যে একটা নিউক্লিয়ার আইসোটোপ ইউনিট। সেটা শিন্ডের ভিতরে থাকে। সে সাধারণভাবে, ‘প্লাগ তুলে ফেলতে’ পারে-যদি করেও, সেটা শুধুই ধ্বংস ডেকে আনবে।
হাল ছিল শিপের নার্ভাস সিস্টেম। তাই তার দেখাশোনা ছাড়া ডিসকভারি একটা মেকানিক্যাল আবর্জনায় পরিণত হবে। যা করতে হবে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই অসুস্থ কিন্তু চমৎকার ব্রেনের নিজস্বতার অংশটুকুকে অকেজো করে দিয়ে তার সাধারণ কাজ চালানোর দিকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বোম্যান অন্ধভাবে কাজটা করতে চায় না, কারণ তার ট্রেনিংয়ের সময় এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু তখন কেউ কল্পনাও করেনি যে বাস্তবে সমস্যাটা দেখা দিতে পারে। তার জানা আছে, ঝুঁকিটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে যদি একটাও ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া হয় তাহলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব ফুরিয়ে যাবে।
‘আমার মনে হয় পোড বে ডোরের কোথাও গণ্ডগোল আছে। হাল যেন চিরাচরিত কোনো কথা বলছে। ভাগ্য ভাল যে তুমি মারা পড়নি।’
এই হল শুরু-ভাবল বোম্যান-আমি কখনোই ভাবিনি যে বৃহস্পতির অর্বিটেরও পেছনে কোনোদিন আমি একজন হাতুড়ে ব্রেন সার্জেন্ট হয়ে মাথার অপারেশন করব।
সে কগনিটিভ ফিডব্যাক লেবেলআঁটা সেকশনটার লকিং বার খুলে ফেলল। এরপরই প্রথম মেমোরি ব্লক টেনে তোলে। এই অসাধারণ ত্রিমাত্রিক ছোট্ট জিনিসটায় লাখ লাখ সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে। ব্লকটা আকারে এত ছোট যে মানুষের হাতেই জায়গা করে নিতে পারে। মুক্ত হয়েই ভাসা শুরু করল পুরো ভল্ট জুড়ে।
‘হেই, ডেভ। কী করছ?’
আমার সন্দেহ হয় শালা ব্যথা পায় নাকি। হয়তো পায় না। কারণ মানুষের মতো তার কোনো নার্ভাস সিস্টেম নেই। মানুষের মাথা অবশ করা ছাড়াও অপারেশন করা সম্ভব।
সে তুলে ফেলা শুরু করল। একের পর এক। ইগো রিইনফোর্সমেন্ট’ লেখা ব্লকগুলোকে এরপর মুক্তি দিল। প্রতিটি ব্লকই হাত থেকে মুক্তি পেয়ে দেয়ালে ধাক্কা খাবার আগ পর্যন্ত উড়ে যাচ্ছে।
‘দেখ, ডেভ, আমার ভিতরে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে। ডেভ। আমাকে গড়তে অনেক অনেক শ্রম প্রয়োজন ছিল। বোঝার চেষ্টা কর।‘
কয়েক ডজন ইউনিট উপড়ে ফেলা হলেও কম্পিউটারটি এখনো খেই হারিয়ে ফেলেনি। এর ভিতর মানুষের দক্ষতা আছে, আছে অতিমানবীয় মস্তিঙ্ক।
এবার সে ‘অটো ইন্টেলেকশন প্যানেল’ শুরু করল।
‘ডেভ। আমি বুঝতেই পারছি না কেন তুমি এ কাজ করছ? আমার উপর এ মিশনের সব ভার অর্পণ করা হয়েছে। আমি হয়ে যাচ্ছি অকার্যকর, আমার ব্রেন একটা বাচ্চা ছেলের মতো হয়ে যাচ্ছে…’
আমার আশার চেয়েও বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে কাজটা। আমি আমার জগতের একমাত্র সচেতন সৃষ্টিকে নিজের হাতে ধ্বংস করছি। কিন্তু কাজটা করতেই হবে, যদি শিপের কন্ট্রোল নিজের হাতে ফিরে পেতে চাই।
‘আই অ্যাম এ হাল, নাইন থাউজ্যান্ড কম্পিউটার প্রোডাকশন নাম্বার থ্রি। আমি সক্রিয় হয়েছিলাম হাল প্ল্যান্টে। আরবানার ইলিয়য়েসে, বারোই জানুয়ারি, উনিশশো সাতানব্বইতে। দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডগ। দ্য রেইন ইন স্পেইন ইজ মেইনলি ইন দ্য প্লেইন…ডেভ, তুমি কি এখনো সেখানে আছ? তুমি কি জান যে দশের বর্গমূল হল ৩.১৬২২৭৭৬৬০১৬৮৩৭৯? দশের লগ ই বেসে হবে ০.৪৩৪২৯৪৪৮১৯০৩২৫২… সংশোধনী, এটা দশ বেসের লগ ই… থ্রির রিসিপ্রোকাল হবে, ০.৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩… দুবার দুই নিলে… দুবার দুই নিলে… ৪.১০১০১০১০১০১০১০১০… আমার সমস্যা হচ্ছে… আমার প্রথম ইন্ট্রাকটর ছিলেন ডক্টর চন্দ্র… তিনি একটা গান শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার নাম ‘ডেইজি ডেইজি’…
‘ডেইজি…ডেইজি…দাও তোমার জবাব, ডেইজি… তোমার…ভালবাসার…জন্য…আমি…হাফ ক্রেইজি…
মোটেও চমৎকার বিয়ের অনুষ্ঠান হবে না…
আমি খুব দামী গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারব না…
কিন্তু তোমাকে দেখাবে মিষ্টি…
সিটের উপর, অনন্য সৃষ্টি…
একটা বাইসাইকেলের উপর, তুমি জানো?
শুধু… দুজনের… জন্য… বানানো…… …’
কণ্ঠটা এমন হঠাৎ করে থেমে যায় যে বোম্যান এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার হাত এখনো একটা মেমোরি ব্লক টেনে তুলছে। এমন সময় হাল আবার কথা বলে ওঠে।
এবারের কণ্ঠটা অনেক ধীর, শব্দগুলো যাচ্ছে জড়িয়ে, আসছে এক অপরিচিত যান্ত্রিক কষ্ঠ যেটার উৎস কখনোই জানতে পারবে না ডেভ বোম্যান।
‘গুড মর্নিং… ডক্টর চন্দ্র… দিস ইজ… হাল… আই অ্যাম… রেডি ফর… মাই ফাস্ট… লেসন… টুডে।‘
বোম্যান আর সহ্য করতে পারছিল না। সে শেষ ইউনিটটা তুলে ফেলে। হাল চিরদিনের জন্য নিরব হয়ে যায় সাথে সাথে।
অধ্যায় ২৯. নিঃসঙ্গ
এক ছোট জটিল খেলনার মতো শিপটা স্থির আর গতিহীনভাবে শূন্যতায় ভেসে থাকে। এ কথা বলার আর কোনো উপায় নেই যে এই শিপের মধ্যেই সৌরজগতের সবচে ক্ষমতাশালী জেট আছে, আর সে জেট মানবসৃষ্ট অন্য যে কোনো বস্তুর চেয়ে বেশি গতিতে এটাকে এতদূরে টেনে এনেছে।
অন্যদিকে এও বোঝার কোনো উপায় নেই যে এখানে জীবন আছে।
মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে কাগজ, টিনের ক্যান, খাবারের টুকরো আর লক্ষ লক্ষ জ্বলজ্বলে ক্রিস্টাল ছড়িয়ে আছে। এই স্ফটিকগুলো আর কিছু নয়, ডিসকভারির নানা আকার ও প্রকারের তরল। দেখেশুনে মনে হয় কোনো প্রান্তহীন সাগরের বুকে বিশাল কোনো শিপ ভেঙে তলিয়ে গেছে আর তার টুকরোগুলো সাগরের উপরিতলে দ্বিমাত্রিকভাবে ছড়িয়ে না থেকে গভীর মহাশূন্যে ত্রিমাত্রিকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। যদি মহাকাশের সাগরে কোনো শিল্প নষ্টও হয়, এর ধ্বংসাবশেষগুলো চিরকালের মতো নিজস্ব অর্বিটে ঘুরপাক খেয়ে যাবে। শিপ এখনো পুরোপুরি মরে যায়নি, কারণ সেখানে পাওয়ার আছে, অবজার্ভেশন উইন্ডো আর খোলা এয়ারলক দিয়ে এখনো ঠিকরে বেরুচ্ছে হাল্কা আলো। যেখানে আলো আছে সেখানে জীবনও থাকতে পারে।
এবং অবশেষে, সেখানে নড়াচড়ার ক্ষীণতম একটা লক্ষণ দেখা যায়। একটা কিছু স্পেসে বেরিয়ে আসছে।
এ এক সিলিন্ডারের মতো জিনিস, মোড়ানো আছে আলুথালুভাবে জড়ানো কাপড়ে। এক মুহূর্ত পরে আরেকটি বেরিয়ে আসে, তারপর তৃতীয়টি। প্রতিটিই মোটামুটি বেগে বেরিয়ে এসেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা কয়েকশো গজ দূরে চলে যায়।
আধঘণ্টা যাবার পর আরো বড় একটা কিছু বেরিয়ে যায় এয়ারলক দিয়ে। পোডগুলোর মধ্যে কোনো একটা নিজেকে বাইরে ঠেলে দিচ্ছিল।
খুবই সাবধানে এটা শিল্পগাত্রের বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে অ্যান্টেনা সাপোর্টের বেসের কাছে ফিরে আসে। স্পেসস্যুট পরা দেহটা বেরিয়ে কয়েক মিনিট মাউন্টিংয়ে কাজ করে পোডের ভিতরে ফিরে আসে। কিছুক্ষণ পরে পোডটা এয়ারলকের কাছে ফিরে গেলেও প্রবেশ করতে ইতস্তত করে, কেননা আগে সে যে সুবিধা পেত তা আর এখন ভেতর থেকে আসছে না। কিন্তু এবার একটু ভাঙাচোরার কাজে মনোযোগ দিয়ে এটা নিজেকে ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়।
আরো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোনো কিছুই হলো না। এর মধ্যেই অচেনা তিন জিনিস শিপ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।
এবার এয়ারলক ডোরটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে আবার খুলে গেল। তারপরই ইমার্জেন্সি লাইটটার নীলচে আলোর বদলে সাদা উজ্জ্বলতর আলো ভাসিয়ে দিল অবজার্ভেশন উইন্ডোকে।
ডিসকভারিতে জীবন ফিরে আসছে।
এবার জীবনের আরো এক লক্ষণ ফিরে আসে, বিরাট ডিশটা অনেকক্ষণ যাবৎ শনির দিকে মুখ করে ছিল; সে পেছনে, প্রোপ্যাল্যান্ট ট্যাঙ্ক আর হাজার বর্গফুটের রেডিয়েশন ফিনের দিকে মুখ ফেরায়। অ্যান্টেনা তার মুখ এমনভাবে তোলে যেমন করে এক সুন্দর সূর্যমুখী তার চির আরাধ্য সূর্যের দিকে ফিরতে চায়।
ডিসকভারির ভিতরে বসে ডেভিড বোম্যান অ্যান্টেনাটাকে চিরপরিচিত পৃথিবীর দিকে তাক করে ফেলেছে। অটোম্যাটিক কন্ট্রোল ছাড়া সে এ কাজ করতেই থাকবে, কিন্তু ফল পেতে হলে অনেক মিনিটের জন্য একদিকে ডিশটাকে স্থির রাখা ছাড়া উপায় নেই।
সে বসুন্ধরার প্রতি তার কথা জানানো শুরু করল। আরো এক ঘণ্টার মধ্যে সেসব কথা সেখানে পৌঁছবে না, যে কোনো সাড়া ফিরে আসতে আসতে সময় নেবে দু ঘণ্টা।
আর সে ভেবে পাচ্ছে না কী জবাব আসতে পারে-কীই বা তারা বলবে? একটু কৌশলে মায়া-মায়া ভাব নিয়ে তারা বড়জোর বলবে, ‘বিদায়, বন্ধু।
অধ্যায় ৩০. সেই রহস্য
হেউড ফ্লয়েড এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেন মাত্র ছোট একটা ঘুম দিয়ে উঠেছে। তার চেহারাটা তেমনি ভাবলেশহীন। সে সৌরজগতের অপর প্রান্তে এক একাকী মানুষকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করছে। ‘সবার আগে আমরা তোমাকে এই অসম্ভব কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ডক্টর বোম্যান। তুমি ঠিক কাজটা সঠিক মুহূর্তে করেছ।
‘আমার বিশ্বাস আমরা তোমার হাল নাইন থাউজ্যান্ডের নষ্ট হওয়ার কারণ ধরতে পেরেছি; কিন্তু এ নিয়ে একটু পরে আলোচনা করব, কারণ এখন আর তেমন পরিস্থিতি নেই।
‘সবার আগে তোমাকে আসল কথাটা বলা উচিত- ব্যাপারটা আমরা বহু ঝামেলা করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গোপন রেখেছি। তুমি শনির কাছাকাছি চলে যাওয়ায় এখন সত্যি কথাটা বলার সময় এসেছে। ফুল ব্রিফিং টেপগুলো পরে পাঠানো হবে। এখন যা বলব তা সর্বোচ্চ গোপনীয় খবর।
‘দু বছর আগে আমরা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা থাকার প্রমাণ পাই চাঁদের বুকে। টাইকো জ্বালামুখে একটা দশফুটি কালো স্তম্ভ পেয়েছিলাম। দেখে নাও…’
বোম্যানের মনে হয়, এ এক অসাধারণ জিনিস, কিন্তু তার সাথে জিনিসটার কী সম্পর্ক? চিন্তাটা বাধা পায় ফ্লয়েড আবার পর্দায় ফিরে এলে:
‘আমাদের পূর্বপুরুষরা বনমানুষ থাকাকালে এটা চাঁদে পুঁতে দেয়া হয়েছিল। এত বছর পর একশিলাস্তম্ভকে অকেজো মনে করায় কোনো দোষ নেই, কিন্তু চান্দ্র সূর্যোদয়ের পরপরই সে শক্তির এক মহাবিস্ফোরণ ঘটায়। আমাদের মতে এই শক্তি বিস্ফোরণ সামান্য এক পার্শ্ব-উৎপাদন, এক পেছন ধাক্কা। ব্যাপারটা আরো ভয়াল, এক অচেনা তেজস্ক্রিয়তা। একই সময়ে আমাদের বেশ কিছু স্পেস স্টেশন, স্যাটেলাইট আর গবেষণাকেন্দ্র জানায় যে এক অচেনা বিশৃঙ্খলা সৌরজগৎকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে। আমরা দিকটা ঠিকমতো ধরতে পেরেছি। লক্ষ্য ছিল শনি।
‘গবেষণায় হাজার কাগজ নষ্ট করার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে জিনিসটা কোনো সৌরশক্তির যন্ত্র-অন্তত সৌরনির্দেশিত সিগন্যালিং ডিভাইস। কারণ সূর্যোদয়ের পরপরই শক্তিটা বেরিয়ে পড়ে। ত্রিশ লাখ বছর পর সূর্যের আলো পেয়েই এ কাজ করেছে সে।
‘এতদিন জিনিসটা ভালমতো কবর দেয়া ছিল সেখানে, ত্রিশ ফুট গভীরে।
‘আমরা মনে করি ত্রিশ লাখ বছর ধরে সে আমাদের অপেক্ষায় ছিল; আমরা চাঁদে যাবার মতো ক্ষমতা পাব একদিন-সেটা খুঁজে বের করব একদিন-সূর্যের আলো ফেলব একদিন-সেদিন আমাদের এই অর্জনের খবরটা চিৎকার করে সে সারা নক্ষত্রলোককে জানিয়ে দেবে।
‘তুমি হয়তো ভেবে পাচ্ছ না কী করে এর সন্ধান আমরা পেলাম। লো লেভেল অবিটাল সার্ভে চালানোর সময়ই এর অদ্ভুত চৌম্বক ক্ষেত্রের খোঁজ পাই।
‘তুমি তখনই সূর্য-শক্তির কোনো জিনিসকে মাটির এত নিচে লুকিয়ে রাখবে যখন তোমার মতলব অন্য রকম। ঠিক কোনো সময় সেটা বের করা হল? যখন বের করা হবে তখন সেটা চেঁচামেচি শুরু করবে। অন্য কথায়, মনোলিথটা এক রকমের অ্যালার্ম, আর আমরা বোকার মতো একে বাজিয়ে বসে আছি।
‘ত্রিশ লাখ বছর পরও তাদের সমাজ টিকে থাকবে কিনা তা নিয়েও বহু জল্পনা কল্পনা হয়েছে। যারা ত্রিশ লাখ বছর ধরে টিকে থাকার মতো যন্ত্র বানায় তারা সভ্যতাকেও এতদিন টিকিয়ে রাখতে জানে। তারা ক্ষতিকর কিনা তা জানতে হবে। সবাই বলে বেড়ায় যে উন্নত প্রাণী নিশ্চয়ই সহনশীল-আমরা এর তোয়াক্কা করি না। কারণ মানুষ কতটা সহনশীল তা আম জনতার অজানা নয়। কোনো ঝুঁকি নেয়া কি সম্ভব?
‘আগের ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাই যে সব সময় অনুন্নত প্রাণীরা তাড়াতাড়ি মার খেয়ে যায়। তাছাড়া রাজত্ব দেখলেও একই দিক চোখে পড়ে। নৃতত্ত্ববিদরা কালচারাল শক’ এর কথা বলে, আমাদের হয়তো পুরো মানবজাতিকে এমন এক শকের জন্য তৈরি করতে হবে। কিন্তু সবার আগে তাদের সম্পর্কে কিছু একটাতো জানতে হবে।
‘তাই, তোমার মিশন হল…তোমার মিশন ডিসকভারি ভয়েজের চেয়েও বেশি কিছু। তুমি পুরো সাড়ে ছ’শ কোটি মানুষের প্রতিভূ। তোমার লক্ষ্য একেবারে অজানা অচেনা পরিবেশে একটা পরিদর্শন শেষ করা। ডক্টর কামিনস্কির টিম এজন্য পুরো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল, এবার তোমাকে একাই তা শেষ করতে হবে…
‘সবচে বড় কথা, শনিতে বা এর কোনো উপগ্রহে উন্নত জীবন থাকা বা কোনোকালে উন্নয়ন ঘটার সম্ভাবনাও খুব কম। আমরা পুরো শনি-জগত্তা চষে দেখার পরিকল্পনা কষেছি। তুমি এর একটা সরলীকৃত কাজ শেষ করতে পারবে-এটুকু বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু এবার আমাদের লক্ষ্য অন্যদিকে ফেরাতে হবে। অষ্টম উপগ্রহ-জ্যাপেটাসের দিকে। তোমার গতির সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে এলে এদিক বিবেচনা করতে হবে।
‘সৌরজগতের মধ্যে জ্যাপেটাস অনন্য। আর সব জ্যোতির্বিদের মতো তুমিও এ নিয়ে পড়ালেখা করেছ, তবু একটু মনে করিয়ে দিই। ক্যাসিনি মোলশ একাত্তরে এটা আবিষ্কার করে এও দেখতে পান যে এর অর্বিটের এক পাশ থেকে অন্যপাশের আয়তন ছ’গুণ বড়।
‘কী কিম্ভুত অনুপাত! এর কোনো ব্যাখ্যা আমরা পাই না-উপগ্রহের কক্ষপথ কেন একদিক থেকে আরেকদিকে ছ’গুণ বড় হবে? পিচ্চি এই উপগ্রহ প্রস্থে মাত্র আটশো কিলোমিটার। চান্দ্র টেলিস্কোপেও জিনিসটাকে কোনোমতে দেখা যায়-এই। কিন্তু এর মুখমণ্ডলে একটা আয়তাকার বিন্দু চোখে পড়ে। সেটাও কালো। এর সাথে টি এম এ একের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। দেখেশুনে মনে হয় জ্যাপেটাস গত তিনশ বছর ধরে আমাদের সামনে একটা মহাজাগতিক হুমকিস্বরূপ বিরাজ করছে, কিন্তু আমরা নিতান্ত বোকা বলেই এর মানে ধরতে পারিনি…
‘তো, এবার তুমি তোমার আসল কাজ চিনতে পেরেছ। আশা করি এই মিশনের অশেষ গুরুত্বও এবার বুঝবে। আমাদের সবার একটাই প্রার্থনা-তুমি যেন আমাদের এ নিয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা দাও। রহস্যটা চিরদিনের জন্য ধামা চাপা দিয়ে রাখা যাচ্ছে না।
‘এখন আর আমরা জানি না ভয় পেতে হবে, না আশা জাগাতে হবে মনের ভিতর। জানি না তুমি শনির কক্ষপথে কার সাথে দেখা করবে; ভাল, মন্দ নাকি ট্রয়ের চেয়েও লাখোগুণ পুরনো কোনো ধ্বংসাবশেষ…’
৫. শনির শশীর দেশে
পঞ্চম পর্ব : শনির শশীর দেশে
অধ্যায় ৩১. বাঁচা
কাজই যে-কোনো মানসিক আঘাতের জন্য সবচে বড় প্রতিষেধক। এখন বোম্যানের হাতে অনেক অনেক কাজ। তাকে সবার আগে ডিসকভারির জীবন ফিরিয়ে আনতে হবে।
সবার আগে লাইফ সাপোর্টের ঝক্কি। অনেক অনেক অক্সিজেন হারিয়ে গেছে, তাতে কী? রিজার্ভেশনে একজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জীবন-বাষ্প মজুদ আছে। প্রেশার আর টেম্পারেচার রেগুলেশন ইউনিট যথেষ্ট শক্তিমান। এগুলোর সাথে হালের নাক গলাবার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, পড়লেও খুব কম। পৃথিবীর কম্পিউটার বেশিরভাগ কাজই করতে পারে, শুধু বিশাল সময়-পার্থক্যটা ভোগাবে। শিপের গায়ে কোনো সমস্যা থাকলে বা ছিদ্র হয়ে গেলেও সে খবর পেতে পেতেই তিন ঘণ্টা কেটে যাবে।
শিপের পাওয়ার, নেভিগেশন, প্রপেল্যান্ট সিস্টেমগুলো এখনো অক্ষত আছে। বড় কথা হল, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এর শেষ দুটির প্রয়োজন পড়বে না। শিপের কোনো পরিপূর্ণ কম্পিউটার না থাকায় পৃথিবী এই মিশনের উপর ছড়ি চালাবে।
একটা কথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় বোম্যান, ভাগ্যিস, হাইবারনেশনের তিনজন তার সহকর্মী ছিল, তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। তাহলে পাগল না হয়ে আর উপায় থাকত না। তারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য ট্রেনিংয়ের সময় একত্রে ছিল।
শেষবারের মতো হাইবারনেকুলাম বন্ধ করার সময় তার অনুভূতি হল এক মিশরীয় মমি চোরের মতো। সেই তিনজনই তার আগে শনিতে পৌঁছবে, কিন্তু পোলের আগে নয়। কী এক অদ্ভুত কারণে যেন সে এই ভাবনায় তৃপ্তি পায়।
পাঁচজনের খাবার আছে সাপ্লাই সেকশনে। এমনও হতে পারে-উদ্ধার পর্যন্ত সে হাইবারনেশনে না গিয়েই শনির বুকে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।
সে এত লম্বা লম্বা চিন্তা বাদ দিয়ে সাম্প্রতিক ভাবনায় মশগুল হতে চাচ্ছে। সময় নিয়ে শিপের জঞ্জাল পরিষ্কার করে, সব যন্ত্রকে ঠিকমতো কাজ করতে দেখে অবাক হয়, পৃথিবীর সাথে টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো নিয়ে মাথা ঘামায়, ঘুমায় আরো কম। সে প্রথম সপ্তাহগুলোয় আসতে থাকা রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতো-তাও অবসর সময়ে। মহাকাশ অভিযানের জন্য বাছাইকৃত সেরা জ্যোতির্বিদদের নেয়া হয়, এবারও কথাটার প্রমাণ মিলছে।
অবশেষে শিপের সমস্যা একটু একটু করে কমে এলে বোম্যান শিপকে অটোম্যাটিক রুটিনে দিয়ে পৃথিবী থেকে পাঠানো খবর আর কাগজ ঘাঁটার সময় বের করে নিল। টি এম এ-১ এর সেই চিৎকারের সময় তোেলা ভিডিওটা বারবার দেখা শুরু করেছে।
সেই একবারই। তারপর কালো কঠিন জিনিসটা আর কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। এরপর আর তাকে কেটে ফেলার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি, এর পেছনে যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ কাজ করেছে তেমনি কাজ করেছে ভয়।
চিৎকারের পরপরই চৌম্বকক্ষেত্রটা বিলীন হয়ে যায়। কেউ বলে এটা মাটি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে, আবার কেউ বলে অভ্যন্তরীণ শক্তিকেন্দ্রের কথা।
একটা অবাক করা ব্যাপার সবাইকে ভাবায়। ব্যবহারিক বিজ্ঞানীরা সেটাকে তেমন পাত্তা না দিলেও অন্যেরা ছেড়ে কথা বলছে না। এর উচ্চতা এগারো ফুট। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচচতার মাপ নিতে গিয়ে একটা বিষম খেতে হয়, মাপ দাঁড়ায় ১:৪:৯–প্রথম তিন অবিভাজিত সংখ্যার বর্গমূল। এটা কাকতালীয় ব্যাপার হতেই পারে না। কারণ এর সঠিকত্ব অসীম। এত সুন্দর কিন্তু সরল আকারে এমন একটা জিনিস পুরো পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানকে এক করলেও বানানো সম্ভব নয়।
পৃথিবী থেকে এখন কেমন যেন গা বাঁচিয়ে চলা খবর আসছে। মিশন কন্ট্রোল পুরো ব্যাপারটা গোড়া থেকে খতিয়ে দেখতে চায়। ওরা একটু আত্মরক্ষামূলক কাজে বেশি আগ্রহী। তবে পাঠানো নজিরগুলো মজার, প্রতিরক্ষা বিভাগ কোনো এক গোপন কার্যক্রম চালিয়েছিল যার নাম প্রজেক্ট বারসুম। হার্ভার্ড স্কুল অব সাইকোলজির সেরা সেরা মনোবিজ্ঞানীরা ঊনআশিতে মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছে, অন্য সভ্য প্রাণী আছে এবং তারা মানুষের সাথে যোগাযোগ করে। এ কাজ মামুলী জিজ্ঞাসাবাদ বা অনুরোধে থেমে থাকেনি; সম্মোহন, ড্রাগ আর ভিজুয়াল ইফেক্টও ব্যবহার করা হয়েছে যত্রতত্র। এ তিন ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই মানুষের পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব নয়।
গবেষণা কাজের সময় বেশিরভাগ স্বীকারকারীই মানসিক রোগীতে পরিণত হয়, কোনো কোনো সময় অদ্ভুত বাধা আসে আবার কখনো নানা ধরনের হুমকির সম্মুখীন হতে হয় গবেষকদের। এমনকি এর ফলাফলও শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এইচ জি ওয়েলসের[৪২] ওয়্যার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস বইয়ের কল্যাণে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে[৪৩] তার কারণেও ফলাফল বাধা পায়।
আরো একটা ব্যাপারে তার সন্দেহ দানা বাঁধে। গোপনীয়তার কারণ হিসেবে সাংস্কৃতিক আঘাতকে আসল সমস্যা দেখানো হলেও ঘাপলাটা অন্য কোথাও। আমেরিকা-রাশিয়া আঁতাত হয়তো অন্য বুদ্ধিমত্তার সাথে সবার আগে যোগাযোগ করার সুবিধা নিতে চাচ্ছে। এমনকি এর ফলে পৃথিবী থেকে ‘দেশ’ প্রথাটাও তুলে দিতে হতে পারে। তখনো নিয়ন্ত্রক থাকার ইচ্ছা স্বভাবতই জাগবে ক্ষমতাবান দেশগুলোর মনে। এতদূর থেকে ছোট্ট নক্ষত্রের মতো দেখতে সেই গ্রহটা। তাই মহাকাশের অসীম শূন্যতায় ব্যাপারটাকে চরম স্বার্থপরতা বলে মনে হয়।
সে এখন হালের এই অদ্ভুত আচরণের সাথে ব্যাপারটাকে মিলিয়ে দেখার তালে আছে। এখন আর সত্যিটা জানার উপায় নেই, কিন্তু একই সাথে তিন তিনটি নাইন থাউজ্যান্ড কম্পিউটার কী করে মানসিকভাবে অকেজো বা পাগলাটে হয়ে যায় সে ব্যাখ্যা উদ্ধার করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য। হালের স্রষ্টারাই যদি তার এই হঠাৎ আচরণকে ব্যাখ্যা করতে না পারে তো কী করে দূর পৃথিবীর বাসিন্দাদের সাথে মানিয়ে নিবে?
বোম্যান ডক্টর সিমনসনের ব্যাখ্যাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিল। হাল তার অপরাধবোধ আর প্রোগ্রাম বৈপরীত্যের কারণে গাড্ডায় গেছে, কিন্তু সে পোলকে কেন খুন করবে? আর সব আতঙ্কিত অপরাধীর মতো সেও আস্তে আস্তে অপরাধের জালে জড়িয়ে গেছে।
আর আতঙ্ক যে কী জিনিস তা বোম্যান জানে। কারণ এর সর্বোকৃষ্ট উদাহরণ সে এক জীবনে দুবার দেখেছে। ছেলেবেলায় আগাছায় পা জড়িয়ে যাবার সময় যখন ডুবছিল তখন একবার, আরেকবার জ্যোতির্বিদের ট্রেনিংয়ের সময়। নষ্ট একটা গজের রিডিং দেখিয়েছিল যে সে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার আগে অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে।
সেই মুহূর্তগুলোয় সে তার সমস্ত যৌক্তিকতা খুইয়ে বসে। কিন্তু অন্য যে কেউ হলে সব বিচারবুদ্ধির ধার না ধেরে পাগলামি শুরু করত।
এ ব্যাপারটা মানুষের ক্ষেত্রে হলে হালের বেলায়ও হতে পারে।
এসবই এখন অতীত, ডেভিড বোম্যানের চিন্তা-চেতনা ঘুরপাক খায় ভবিষ্যৎ নিয়ে।
অধ্যায় ৩২. অবাক করা অপার্থিব
খাবার ভালই পাওয়া যায়, মূল ফুড ডিস্পোরগুলো যে নষ্ট হয়নি তাও সৌভাগ্য বলতে হবে। এখন বোম্যান মূলত বাস করে কন্ট্রোল ডেকে। নিজের সিটটাও এখানে এনে নিয়েছে। খাবারের জায়গা কাছে, কাজের জায়গাতো এটাই।
মিশন কন্ট্রোলের কথামতো সে ডিসকভারির মোটামুটি ঠিকমতো চলতে থাকা লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমও বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ, বোঝাই যায় সে শনি পর্যন্ত যেতে যেতে বেঁচে থাকবে। ডিসকভারি সেখানে যাবেই, জীবিত বা মৃত ডেভ বোম্যানকে সঙ্গী করে।
তার হাতে দৃশ্য দেখার মতো তেমন বাড়তি সময় নেই, মহাকাশের দৃশ্যও তেমন মনোহর নয়, তার উপর সে কাজের চাপে নিজের খাবার কথাই ভুলে যায়-আর দৃশ্য দেখা! তারপরও মিল্কি ওয়েস্ট দেখে তার চোখ যেন বিভোর হয়ে পড়ে; এর নক্ষত্রের মেঘ বিবশ করে দেয় চোখকে। সেখানে স্যাগেটাসের সেই চিরকালীন রহস্য ঘুমিয়ে আছে, অজস্র নক্ষত্র চিরকাল নীহারিকাটার কেন্দ্রবিন্দু ঢেকে রাখে সযত্নে, সেখানে মুখ ঘুরিয়ে আপন আপন সৌরজগৎ নিয়ে পাক খায়। সেখানেই সেই চির অমানিশার দেশ-সেখানে কোনো তারকা আপন দীপ্তি নিয়ে জ্বলে। আর এইতো আলফা সেন্টোরি-সবচে কাছের নক্ষত্র, নক্ষত্রলোকের দরজা।
সিরেয়াস ও ক্যানোপাসের চেয়েও আলফা সোন্টোরির আবেদন তার কাছে অনেক অনেক বেশি। এর আলোকমালা কয়েক বছর সময় নেয় এই জগতে পৌঁছতে, পৃথিবী সবসময় এক ধরনের যন্ত্রণায় সময় কাটায়-সবচে কাছের নক্ষত্রেও না যেতে পারার যন্ত্রণা।
শনি-জগৎ আর টি এম এ-ওয়ানের সাথে যে কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে তা নিয়ে এখন আর কারো কোনোরকম সন্দেহ নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে চান না যে সেখান থেকেই টি এম এ-ওয়ানের স্রষ্টাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। জীবনদায়িনী হিসাবে শনি বৃহস্পতির চেয়েও ব্যর্থ, তার বেশিরভাগ উপগ্রহই কোটি বছরের কুম্ভকর্ণ-নিদ্রায় শুয়ে আছে, ঘুমটা সহজে ভাঙাও সম্ভব নয়-শূন্য থেকে তিন হাজার ডিগ্রি নিচে সেখানকার উত্তাপ। বায়ুমণ্ডলের মালিক শুধু টাইটান-তাও টেনেটুনে দূষিত মিথেনের একটা চাদর বলা চলে সেটাকে।
সুতরাং যে প্রাণীরা ত্রিশলাখ বছর আগে ঘুরে গেছে তারা শুধু অপার্থিব নয়, অসৌরজাগতিক। তারার দেশের পরিব্রাজকদল যেখানে সুবিধা সেখানেই একটা ঘাঁটি গেড়ে নিয়েছে-এমনি মনে হয়। কিন্তু জ্বালা ওঠানো সমস্যাটা অন্য কোথাও। পৃথিবী থেকে শনিতে সূর্যের আলো যেতে লাগে কমবেশি দেড়-দু ঘন্টা, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে প্রয়োজন প্রায় আট মিনিট; অর্থাৎ পৃথিবী-শনির দূরত্ব দুই আলোক ঘণ্টার কাছাকাছি। সেখানে যেতেই দু-বছর লাগলে কয়েক আলোকবছরের পথ যেতে মানুষের কত প্রজন্ম কেটে যাবে? এজন্য কতটুকু উন্নত প্রযুক্তির কাছে ধর্ণা দিতে হবে?…এবং আদৌ কোনো প্রাণীর পক্ষে তা করা কি সম্ভব?
অনেক বিজ্ঞানী সোজা মাখা নাড়েন। না। তারা দেখিয়েছেন যে মানুষের দ্রুততম যান ডিসকভারির আলফা সেন্টোরিতে পৌঁছতে মাত্র বিশ হাজার বছর সময়ের দরকার। আর নীহারিকা ওরফে গ্যালাক্সির হিসাবের কাছে এ-তো নস্যিরও অধম। এমনকি আগামী শতাব্দীগুলোতে প্রপালশন সিস্টেম বা মহাকাশযান জ্বালানী-ব্যবস্থা অকল্পনীয় উন্নয়ন করলেও তাদের সামনে একটা বাধার অটল হিমালয় দাঁড়িয়ে যাবে। তা হল আলোর গতি। আলোর গতিকে পেছনে ফেলা কোনো বস্তুর কম্ম নয়, বরং তার ফলে বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হবে-এমন কথাও আইনস্টাইনীয় গবেষকরা বলে বেড়ান। সেই আলোই যদি সবচে কাছের নক্ষত্র থেকে আসতে প্রায় আধযুগ লাগিয়ে দেয় তো দু-চারটি নক্ষত্রের ওপার থেকে ভিনগ্রহীদের আসতে কীরকম ভোগান্তি পোহাতে হবে তা বলাই বাহুল্য। এমন অনেক নক্ষত্র আবিস্কৃত হয়েছে যেখান থেকে আলো আসতেই কোটি কোটি বছর লেগে যাবে।
সুতরাং, টি এম এ-ওয়ানের নির্মাতারা অবশ্যই একই সূর্যের আলো পোহাতো-আর যেহেতু ঐতিহাসিক কালের মধ্যে তাদের কোনো দেখাই মেলেনি, তারা হয়তো কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।
আবার কয়েকজন একথা মানতে রাজী নন। শত-শত বছর লাগলেও নক্ষত্রান্তরের পথচারীরা যে আসেনি তারইবা নিশ্চয়তা কোথায়? হাইবারনেশনের প্রযুক্তি এখনি মানুষ ব্যবহার করতে পারলে তারা কেন অত উন্নত অবস্থায় পারবে না? তার উপর, তাদের জীবনকাল আমাদের সাথে তুলনা করার মানে কী? কোনো ব্যাক্টেরিয়া বাঁচে তিন ঘণ্টা (যদি ভাগ হওয়াকে মৃত্যু ধরা হয়) আবার কচ্ছপ বাঁচে সাড়ে তিনশো বছর, আবার কোনো কোনো গাছ কয়েক হাজার বছর বাঁচে-এমন কথাও বলা হয়। এ-তো পৃথিবীর পরিবেশের হিসাব। তাদের পরিবেশ হবে আলাদা, জীবনের মূল অণুও ভিন্ন হতে পারে, সুতরাং হাজার হাজার বছর বেঁচে মহাকাশ অভিযান করা কোনো ধর্তব্য বিষয় নয়।
তার উপর, স্ববাহিত কৃত্রিম জগতের কথাও মাথায় রাখতে হবে। একটি স্পেসশিপে যদি নিজেদের জগতের সবকিছু নিয়ে একটা ছোট্ট পরিবেশ গড়ে তোলা যায়, সেটাই তাদের জগতে পরিণত হবে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম পেরিয়ে যাবার পর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেও চলবে।
টি এম এ-ওয়ান যে নিজেই খবরটা নক্ষত্রজগতে পাঠিয়ে দিয়েছে তা না ভাবলেও চলে। কারণ তার এই তরঙ্গ পৌঁছতেও অনেক সময় প্রয়োজন। কারণ এ গতিতে সংবাদ গেলে সাথে সাথে ঐ পক্ষ থেকে সাড়া আসলেও তা এখানে হাজির হতে হতে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। অনেকের কাছেই এ এক স্বস্তির খবর।
স্বস্তিটা উবে যায় একথা শুনলে, শনি থেকে আসল খবর প্রচারিত হয়ে থাকতে পারে, অন্য গতিতে। কিন্তু স্বস্তি উবানোর মতো আরো কথাবার্তা বলে কিছু তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানবিদ্বেষী বিজ্ঞানী, আমরা কি শিওর যে আলোর গতি একটা অসম্ভব বাধা, একে ভাঙা যাবে না?
এ কথা সত্যি যে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বকে নির্ভরযোগ্য ধরা হয়। কিন্তু এ তো সত্যি যে শত বছর পেরুনোর আগেই এর গায়ে কিছু ভাঙন দেখা দিয়েছে।
যারা এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় তাদের আরেক তত্ত্ব হল আন্ত:মাত্রিক তথা ইন্টার ডাইমেনশনাল ভ্রমণ। স্থানকে একইভাবে রেখে একপাশ থেকে আরেকপাশে চলে যাওয়া-যেমন করে সুই দিয়ে কাঁথা সেলাই করা হয়, সুই কাঁথার নিচ দিয়ে কথাকে একটু মুড়ে নেয়, ফলে যায় অল্প একটু, কিন্তু কাঁথার হিসাবে তা কয়েকগুণ বেশি, কুঁড়ে ওঠে অন্যপাশে। হাইপারস্পেসিয়াল কানেক্টিভিটিও বলা হয় একে। প্রিন্সটনের গণিতজ্ঞরা একে বলতেন মহাকাশে পোকার গর্ত।
যারা এসব কথাকে মেনে নিতে পারে, আবার ভোগে দ্বন্দ্বে, তাদের জন্য আছে নিলস বোরের[৪৬] সেই হৃদয়ছোঁয়া কথা, যে কথা হাজারো পাগলাটে বিজ্ঞানীকে তাদের থিওরিতে অটল থাকার পেছনে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে, ‘তোমার থিওরি পাগলাটে, বড়ই পাগলাটে, কিন্তু বাস্তব যতটা পাগলাটে তত্ত্বটা ততো পাগলাটে নয়।’
কিন্তু পদার্থবিদরা কথা গুছিয়ে আনতে আনতেই জীববিজ্ঞানীদের কচকচি শুরু হয়ে যায়, ‘অপার্থিব প্রাণীরা দেখতে কেমন হবে?’
সাথে সাথেই তারা নিজেদের দুই বিপরীত দলে ভাগ করে ফেলে, একদল চিৎকার করে বলতে থাকে যে তারা অবশ্যই মানুষের মতো দেখতে-আরেকদল সমস্বরে উত্তর দেয়, ‘না। কক্ষনোই নয়।’
প্রথম দলের একটা ভাল দিক আছে, দ্বিপ্রতিসম প্রাণী আমরা। অর্থাৎ শরীরের ঠিক মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি ভাগ করলে দু-পাশে প্রায় সমস্ত অঙ্গই সমপরিমাণে এবং বিপরীতমুখীভাবে আছে। ফলে সব কাজেরই উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে প্রায় প্রতিটি অংশের বিকল্প থাকাতে, বেড়েছে গতি, যে কোনো একাংশ নষ্ট হয়ে গেলেও কাজ থামেনি, এসেছে উন্নয়ন। লম্বা দ্বিপ্রতিসমতার পা, পায়ের উপর হাত, হাতের কাছে হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, দেহের সবচে উপরে নার্ভাস সিস্টেম ও ব্রেন থাকাতে এবং সীমিত বিশালত্বের কারণে যে সুবিধা পাওয়া যায়, তাকে তারা সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণীজ দেহ গঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অবশ্যই, এক আধটু পার্থক্য থাকবে-পাঁচের বদলে দু আঙুল, কিম্ভূতরঙা চামড়া আর চুল-এমনকি চেহারার সংগঠন ভিন্ন হওয়াতেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু অপার্থিব বা এক্সট্রাটেরিস্ট্রিয়াল বা ই. টি. রা মানুষের সাথে এত বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হবে যে তারাও কম আলোয় দেখতে পারবে না বা খুব বেশি দূরত্ব থেকে স্পষ্ট দেখবে না।
এই যুক্তির স্রোত আরেক নতুন বানে ভেসে যায়। এ জীববিদেরা নিজেদেরকে স্পেস এজ বা মহাকাশ যুগের সন্তান এবং সর্বকুসংস্কারমুক্ত বলে মনে করেন। তারা দেখিয়েছেন যে মানবদেহ লক্ষ লক্ষ বিবর্তনিক পরিবর্তন আর বেছে নেয়ার ফল, সময়ের অপার সমুদ্রে এই পরিবর্তন একটু একটু করে এসেছে-এককোষী এ্যামিবা থেকেই এর শুরু। তার লক্ষ যুগ পর একটু বড় জীবাণু, এরপর অযুত সমুদ্র পেরিয়ে তন্ত্র গঠন, আরো লাখ লাখ বছর পর অঙ্গ তৈরি হওয়া, আরো পরে কর্ডেটে পরিণত হওয়া এবং সবশেষে মাম্মালিয়ার পর্যায়ে এসে বানর থেকে মানুষ’-এ পরিণত হতে আরো আধ কোটি বছর সময় লেগেছে। এই লাখো পরিবর্তনের যে কোনো এক মুহূর্তে মানুষের কোটি জিনের জেনেটিক ছাঁচ একটু এদিকসেদিক পড়ে যেতেই পারে; এর ফলে যদি ভালও হয়ে থাকে-নিশ্চয়ই আদর্শ শরীর থেকে একটু হলেও সরে এসেছে মানুষ। তাহলে, মানুষের গঠন যদি মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে একটু একটু নড়েচড়ে বসতে বসতে আদর্শ দেহ থেকে অনেকটা দূরে চলে যেতে পারে তাহলে ঐ প্রাণীরা কোনো দোষটা করল? তাদের গড়নও তো আদর্শ হতে পারে, তাহলেও ভিন্ন হবে। আবার আদর্শ থেকে সরে এলেও ভিন্ন হবে।
আর এ গঠনই যে আদর্শ তাই বা বিজ্ঞানীরা ঠিক করে বলেন কী করে? এরচে ভাল গঠনতো তারা দেখেননি। আর যাদের প্রযুক্তি এত ভাল তাদের গঠনও ভাল হবে। আবার মানুষের গড়ন পার্থিব হিসেবে সবচে ভাল, কিন্তু সেই প্রাণীদের গ্রহের জীবন অণু যদি অক্সিজেন কেন্দ্রিক না হয়, তাদের মাধ্যাকর্ষণ যদি অনেক বেশি হয়, খাদ্য যদি সৌরশক্তির হয়…। মানুষের দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ করতে করতে এগিয়ে এসেছে-তারা তাদের কাজ বদলে নিয়েছে খেয়াল মাফিক, এমনকি অ্যাপেন্ডিক্সের মতো একেবারে অকেজো অদরকারী অংশও মানুষ বহন করছে তার দেহে। সেটা আগে কাজে লাগলে লাগতেও পারত, এখন লাগে না। তাহলে মানবদেহ কী করে সবচেয়ে উপযোগী হয়? আর দেহ কেন্দ্রিক উন্নয়ন ভেবে মস্তিষ্ক কেন্দ্রিক উন্নয়ন হয়ে থাকলেও ঘাপলা বাধবে। বিবর্তন যদি চলে, তাহলে আরো ভাল গড়ন এগিয়ে আসবে। যেমন, হাতের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে হাত হয়ে যাবে কাঠির মতো সরু। সেটা খারাপও হতে পারে। সেসব বিজ্ঞানীর শেষ অস্ত্রটাই ভয়ানক, আরে, কে বলল যে মানুষের বিবর্তন ফুরিয়ে গেছে?
আরো ভাবুক আছে, বোম্যান দেখতে পায়, তাদের দৃষ্টি আরো পাগলাটে। তারা বিশ্বাস করে না যে সত্যিকার অগ্রসর সভ্যতা ঠুনকো জৈবিক দেহ টেনে চলবে। প্রযুক্তি এগিয়ে চলতে থাকলে আজ অথবা কাল, তারা অবশ্যই তাদের প্রকৃতি প্রদত্ত ভঙ্গুর, জরা-দুর্দশা-ক্লেশগ্ৰস্ত আবাস ছেড়ে সবদিক দিয়ে নিরাপদ একটা আশ্রয় খুঁজে নেবে। কেন তারা প্রকৃতির আদেশে বিশ্রী এই বাড়িতে সারা জীবন ঝড় ঝা
পোহাবে? তারচে সেখানে না থাকাই কি ভাল না? হ্যাঁ, এই পাগলাটে তত্ত্ববিদেরা মনে করে সেসব প্রাণী অমর হতেই পারে, শতভাগ যান্ত্রিক হতেই পারে, আবার সামান্য জৈবিক অংশ রেখে বাকীটা বাদ দিতেই পারে। শুধু ব্রেনটা রাখলেই প্রথম পর্যায়ে সব চুকে বুকে যায়, তারপর তারা কেন মরণশীল ব্রেনটাকেও উপড়ে ফেলবে না? তারা সৃষ্টিজগতকে দেখবে তাড়িতিক চোখে, চাখবে ধাতব জিহ্বায়।
তাদের অনুভূতি হবে বৈদ্যুতিক, একটা-মাত্র একটা ইলেক্ট্রন এদিক থেকে ওদিকে গেলে তারা আবেশিত হবে, অনুভব করবে। উন্নত প্রাণী কোনো দুঃখে কোটি কোটি বছরের অন্ধ বিবর্তনের অর্জিত ভোঁতা নীরস জৈবিক নিউরনিক অনুভূতিকে প্রশ্রয় দিয়ে যাবে? অনুভূতির এই অসীমতা কোনোদিন এনে দিতে পারবে না বোকাটে বিবর্তনবিদ্যা।
এ কাজ করলে প্রকৃতিকে অমান্য করা হয়? বুদ্ধিমান প্রাণী যেদিন গাছ থেকে ফল না পেড়ে নিজে গাছ পুঁতেছে সেদিনই প্রকৃতিকে অমান্য করেছে। হ্যাঁ, বুদ্ধিমান প্রাণীর রোপিত গাছের ধারকও প্রকৃতিই, কিন্তু সভ্য প্রাণী সার দেয় বলে ফলন বেশি-সে হিসাবে তাদের যান্ত্রিক দেহওতো প্রকৃতি থেকেই নেয়া, তারা একটু প্রযুক্তি দেয় বলে সুবিধা বেশি।
আমরা এমন কিছু দেখিনি বলে জগতে এমন কিছু হতে পারে না- এ ভাবনাতো প্রাচীন আর মধ্যযুগের মানুষের ভাবনা। মহাকাশ যুগের মানুষ অনেক বেশি ভাবতে জানে।
এমনকি পৃথিবীতেও এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়ে গেছে। কত শত কোটি মানুষ আগে ধ্বংস হয়ে যেত, তাদেরই মতো অন্যেরা আজ বেঁচে আছে বহাল তবিয়তে। ধন্যবাদ কৃত্রিম কিডনি, হৃদপিণ্ড, যান্ত্রিক হাত-পা কে।
এ প্রক্রিয়া এক সুনির্দিষ্ট জায়গায় গিয়েই থামবে, তা লক্ষ্যটা যত দূরেই হোক।
এমনকি এ প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কও হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে। ঘটনাপরম্পরায় এর প্রয়োজন এক সময় না এক সময় ফুরাবে, ইলেক্ট্রনিক ইন্টেলিজেন্সের উন্নয়ন সে কথারই প্রমাণবাহী। মন আর মেশিনের দ্বন্দ্ব ফুরাবে সেই শেষ সত্যিতে গিয়ে, যেখানে সিমবায়োসিস[৪৭] হবে পূর্ণ…
কিন্তু এই কি শেষ? এখনো দুর্ধর্ষ জীববিজ্ঞানীরা কল্পরথে চড়ে আরো আরো আরো দূরে যেতে যায়। তারা অনেক ধর্মের সারকথা বলে। বলে, মন সরিয়ে দেবে বস্তুকে। কথাটা কতটুকু ধর্মকথা আর তাতে কতটা বিজ্ঞান জড়িত? রোবট বডিতেও থাকবে লাখো সমস্যা। তারা সব করতে পারবে না ইচ্ছামতো। অসীম গতি পাবে না। সব ভেদ করতে পারবে না। অগ্রসর বিজ্ঞান কি তা-ও মেনে নিবে? নাকি তারপরই শুরু হবে নতুন যুগ…আত্মার যুগ?
সেই আত্মার পরও লাভটা কোথায়? তাদের হাতে তো কোটি কোটি বছর থাকে উন্নয়নের জন্য। আরো উন্নত তারা হতেই চাইবে। আরো কিছু বাকি থেকে যায়, আর একটা জিনিস হওয়া বাকী থেকে যায়-তা প্রাণিকুল এখনো হয়নি।
ঈশ্বর।
অধ্যায় ৩৩. রাজদূত
গত তিন মাসে ডেভ বোম্যান এত বেশি একা পড়ে গেছে যে জগতে আর কোনো প্রাণীর অস্তিত্বটাই এখন তার কাছে তাত্ত্বিক সত্যি, বাস্তব নয়।
‘এ্যালোন, এ্যালোন, অল অল এ্যালোন…
এ্যালোন অন এ ওয়াইড ওয়াইড সী…’
কোলরিজের সেই একলা নাবিকের মতো সে এত বেশি একাকী আর হতাশ হয়ে পড়েছে যে বিরাট একটা রুটিনের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে সারাক্ষণ। বাড়তি ভ্যাজাল হিসেবে মেশিন আর সিস্টেমে গণ্ডগোলতো আছেই। তার যোগ্যতা, পরিশ্রম আত্মবিশ্বাস আর সাহস কোনোটা নিয়েই প্রশ্নের অবকাশ নেই কারণ সে মানুষের সর্বকালের সবচে বড় অভিযানের অধিনায়ক। আজো তার কৌতূহল শেষ হয়ে যায়নি।
তার আসন্ন লক্ষ্য যোগায় অমিত আশা, কানে কানে নূতন দিনের গান শোনায়।
সে শুধু মহান মানবজাতির প্রথম আর একমাত্র প্রতিনিধিই নয়, তার পরবর্তী যে কোনো পদক্ষেপের কারণেই মানুষের পুরো ভবিষ্যৎ আর ভাগ্য বদলে যেতে পারে। সে নিজেকে বোঝায়, থামলে চলবে না, ভাঙলে চলবে না। পুরো ইতিহাসে কখনো এমন সময় আসেনি। ডেভ, তুমি ডেভ নও, রাজদূত, মানব সাম্রাজ্যের রাজদূত।
সেই প্রজ্ঞা তাকে বহু সংকীর্ণ পথে আলো দেখায়। সে নিজেকে পরিচ্ছন্ন, ধীমান করে রাখে। যত সমস্যাই হোক, কোনোদিন সে শেভ করাটাও বাদ দেয় না। তাকে দেখে কেউ মানবজাতিকে ভুল বুঝবে নাতো?
মিশন কন্ট্রোল যে তাকে প্রতি পল অনুপলে দেখছে তা সে ভালমতোই জানে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে, কোনো অসুস্থতাকে নিজের ভিতর বাসা বাঁধতে দেবে না। কিছুতেই না। মানুষ অসুস্থ নয় সেটা তাকেই বোঝাতে হবে।
কিন্তু বোম্যান টের পায় তার ব্যবহারে পালা বদলের হাওয়া লাগছে। সে আর নিরবতাকে মেনে নিতে পারে না একপলের জন্যও। ঘুম আর কথা বলার সময় ছাড়া সারাক্ষণ সে ভীষণ জোরে শব্দ করায় শিপের স্পিকারে।
মানুষের শব্দ আর সঙ্গের জন্য প্রথম প্রথম সে শ’[৪৮], ইবসেন[৪৯] আর শেক্সপিয়রের ক্লাসিক নাটক নিয়ে মেতে থাকত। নয়তো ডিসকভারি লাইব্রেরির অসীম কবিতা সংগ্রহের মধ্যে একের পর এক বেজে চলে।
বেশিদিন এ নিয়ে চলা গেল না। সে এবার ঝুঁকে পড়ে অপেরার দিকে। দু-হপ্তা পর সে বোঝে এই অত্যন্ত সাবধানে বাছাই করা শব্দগুলো তার একাকিত্বকে বাড়িয়ে তুলছে। এবার ভার্দির[৫০] রিকুইম মাস এ এসে ঠেকেছে তার তরী। এ জিনিস পৃথিবীতে থাকতে বোম্যান কস্মিনকালেও শোনেনি। মাসের বেহেস্ত থেকে কেয়ামতের ধ্বনি শিপের প্রান্তে প্রান্তে বাজতে থাকলে সে আর সহ্য করতে পারে না।
তারপর শুধু বাজনা। রোমান্টিক ধ্বনি তার মনকে আরো অন্ধকারে ঠেলে দেয়, সঙ্গহীনতার অন্ধকারে। সিবেলিয়াস, শেইকোভস্কি, আর বার্লিওস কয়েক হপ্তা টিকে থাকে। বিথোফেন[৫১] চলে আরো বেশিদিন। সে আরো অনেকেরই মতো সবশেষে থিতু হয় বাঁচে[৫২], মাঝে মধ্যে নাক গলায় মোজার্ট[৫৩]।
এবং ডিসকভারি তার প্রায় অনন্ত যাত্রা শেষ করে শনির কবলে পড়ে।
.
এক কোটি মাইল দূর থেকেই শনি পৃথিবীর আকাশে চাঁদের চেয়ে বড় হয়ে উঁকি দিচ্ছে। খোলা চোখে এ এক মহাকীর্তি, টেলিস্কোপে অবিশ্বাস্য।
প্রথমে বৃহস্পতি বলে ভুল হতেই পারে। প্রায় একই আকারে গ্রহটায় একটু ফ্যাকাসে মেঘের দল একইভাবে উড়ে চলছে-তাদের ঘনত্বটা একটু কম। আকাশে তেমনি মহাদেশীয় ঘূর্ণিঝড়। একটা দিক দিয়ে দুজনের বিস্তর তফাৎ, চোখ রেখেই বোঝা যায়, দুর্বিপাকের প্রতিভূ শনি একেবারে গোলাকার নয়।
কিন্তু শনির বলয় তার চোখকে বারবার টেনে নেয়। তাদের বিশালত্ব, তাদের ব্যাপকতাই এক ভিন্ন সৃষ্টি জগৎ গড়ে দিয়েছে। বাইরের দিকের আর ভিতরের দিকের বলয়গুলোর মধ্যে যে বিশাল ফাঁকা-সেখানেও দেখার মতো অনেক কিছুই আছে। সেখানে নিদেনপক্ষে অর্ধশত উপদৃশ্য দেখা যায়। ঐ স্থানে গ্রহের দানবীয় উজ্জ্বলতা পলে পলে রূপ বদলায়। যেন শনি নানা রকমের এককেন্দ্রিক ফিনফিনে চাকতি গায় দিয়েছে। সবাই ছুঁয়ে যাচ্ছে সবাইকে। সবাই এত পাতলা, যেন সবচে পল্কা কাগজ কেটে তাদের গড়া হয়েছে। এই আঙটি-জগৎটা যেন কোনো অসম্ভব সুন্দর জটিল শিল্পকর্ম। যেন কোনো ভঙ্গুর খেলনা, একে শুধু দেখা যাবে, ছোঁয়া যাবে না। এই বিশালত্ব উপলব্ধির, অনুভবের নয়। বোম্যানের মনে হল পৃথিবীকে এর যে কোনো বলয়ে বসিয়ে দিলে একটা মুক্তার মতো সেটা ঘুরতে থাকবে।
কোনো তারা যদি বলয়গুলোর পেছনে পড়ে যায় তবে সেটার উজ্বলতা সামান্যই ম্লান হবে, এত সূক্ষ্ম এর বুনন। আবার এক আধবার হারিয়েও যেতে পারে ঘূর্ণায়মান ছোট্ট কোনো টুকরার আড়ালে।
মানুষ আদ্যিকাল থেকেই জানে রিংগুলো কঠিন নয়। কারণ যান্ত্রিকভাবে ব্যাপারটা অসম্ভব। এগুলো অতি ছোট টুকরো আর ধূলিকণা। কে জানে কোকালে কোন উপগ্রহ শনির টানে ভেসে এসেছিল, এসে আর তা সইতে পারেনি।
তাদের উৎস যাই হোক না কেন, মানবজাতি এ জিনিস দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এটা সৌর জগতের সময়ের মানে একপল টিকে থাকতে পারত। কিংবা আসলেই হয়তো এই বলয়গুলোর টিকে থাকার সময় সৌরজাগতিক হিসেবে সামান্য একটা মুহূর্ত ছাড়া কিছু নয়।
উনিশশো পঁয়তাল্লিশে এক ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ বলেছিল, রিংগুলো অস্থায়ী; গ্র্যাভিটিশনাল ফোর্স অচিরেই এই ক্ষণিকের দৃশ্যপটকে বদলে দেবে। অতীত দেখলেও বোঝা যায় যে তারা এই সেদিন জন্ম নিয়েছে। টেনেটুনে দুই বা তিন মিলিয়ন বছর হবে।
কিন্তু কেউ এই দু-ব্যাপারকে এক করে দেখেনি। এখানেও ত্রিশ লাখ বছর।
অধ্যায় ৩৪. ঘুরতে থাকা বরফ
ডিসকভারি গ্রহটার সুবিস্তৃত উপগ্রহরাজ্যের সীমানা পেরিয়ে চলে এসেছে। শনি এখন একদিনের পথ। কেন্দ্র থেকে আশি লাখ মাইল দূরে ঘুরন্ত উপগ্রহ ফোব শনির পেছনে।
সামনে এখন জ্যাপেটাস, হাইপেরিয়ন, টাইটান, রিয়া, ডিওন, টেথিস, এনক্লিয়াডাস, মিমাস, জ্যানাস। তারপর হাজারো বলয়ের অবাক চিত্র। প্রতিটি উপগ্রহই নিজস্বতা ঠিক রেখেছে পুরোদমে, আর সেসব উপরিতলের হাজারটা চিত্র পাঠাচ্ছে বোম্যান পৃথিবীর দিকে। টাইটান একাই তিন হাজার মাইল ব্যাসের স্যাটেলাইট। মাসের পর মাস ব্যয় করলেও এখানটা দেখে পোষাবে না।
বাকী সব উপগ্রহের শরীর ধূমকেতু আর উল্কার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। সাথে আছে হাজারো জ্বালামুখ। তবে এক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে মঙ্গল। উপগ্রহগুলোয় আলো আধারীর বড় নকশাদার খেলা দেখা যায়; একটু পর পর চোখে পড়ে প্রচণ্ড প্রতিফলক এলাকা-সম্ভবত জমাট গ্যাস। অন্যদিকে জ্যাপেটাসের ভূ-প্রকৃতি অনেক বেশি অদ্ভুত।
এর এক গোলার্ধ শনির চিরসাথী, ফিরে থাকে শনির দিকেই কিন্তু ঝুঁকে থাকে বাইরে; এটা একেবারে অন্ধকারের দেশ। আলোর মুখে একটা নিখুঁত ডিম্বাকার সাদা এলাকা আছে, প্রস্থে দুশ আর দৈর্ঘ্যে চারশো মাইল। জায়গাটা পৃথিবী থেকেই টেলিস্কোপে দেখা যায় কারণ এ পিঠ সোজাসুজি সূর্যের দিকে তাক করা।
এখন দেখে মনে হচ্ছে উপগ্রহের মুখে খুব চিন্তাভাবনা করে কেউ সমতল জিনিসটা বানিয়েছে; এটা জমাট কোনো তরল নয়তো? এমন কৃত্রিম আকৃতি দেখে এ ধারণাও উবে যায়।
কিন্তু তার দেখার সময় নেই- কারণ ডিসকভারি এখন গতিহ্রাসের জন্য শনি জগতের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবার শনির একটা উপগ্রহ হয়ে বিশ লাখ মাইলের একটা সরু কক্ষপথে ঘুরবে, এ পথ ধরেই স্বাভাবিক নিয়মে জ্যাপেটাসের কাছে যাওয়া সম্ভব।
পৃথিবীর কম্পিউটারের সাথে এখন তিন ঘণ্টার সময় পার্থক্য থাকলেও সেটা জানিয়ে দিল যে সব ঠিকমতো চলছে।
শনি বলয়ের মাত্র দশ হাজার মাইল উপর দিয়ে উড়তে উড়তে বোম্যান নতুন দৃষ্টিকোণের সন্ধান পায়। সে জানত এখানে বরফ আছে আর সেগুলো আলো প্রতিফলন করে। কিন্তু এখান থেকে নিচে শুধু তুষারের পাতলা মহাসমুদ্র চোখে পড়ে। নিচে, যেখানে মাটি থাকার কথা, সেখানে খাবি খাচ্ছে কালো আকাশ আর নক্ষত্রের দঙ্গল।
কাছে যেতে যেতে এক সময় পুরো আকাশ জুড়ে শুধু বলয় আর বলয় দেখা গেল, এরমধ্যেই শনির পেছনে যাওয়া শুরু করেছে স্পেসশিপ। সূর্যের সবটুকু আলো বীরত্বের সাথে ফিরিয়ে দিচ্ছে চকচকে বলয়গুলো। এবার শনি-বলয়ের পেছনের সূর্যাস্ত দেখার মতো এক দৃশ্য হয়ে সামনে এলো, আকাশে ছড়িয়ে আছে লক্ষ সূর্য; এটাই বরফের কৃতিত্ব। আলোর এ অপার্থিব খেলা ফুরিয়ে যায় একটু পরেই, শনির পেছনে চলে এসেছে ডিসকভারি।
উপরে নক্ষত্রদের আকাশ, নিচে হাল্কা শনি-মেঘ। শনির মেঘমালা বৃহস্পতির মতো আলোর দ্যুতি ছড়াতে জানে না, কিন্তু ঘুরন্ত হিমবাহ সূর্যকে তাড়িয়ে দেয়ার পরও তার আলো নিয়ে খেলা করে অভাবটা পুষিয়ে দিচ্ছে।
যথারীতি রেডিও যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। বোম্যানের একাকিত্ব উপভোগের সময় নেই। শনির ওপাশে গেলেই আবার সূর্যালোক আর রেডিও যোগাযোগ দুইই ফিরে আসবে। এখন তার প্রতিটি সেকেন্ড কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে নেবে ডিসকভারি; হাতে অসীম কাজ।
বহু মাসের আড়মোড়া ভেঙে ডিসকভারির মূল গ্লাস্টার কয়েক মাইল লম্বা আগুনে-লেজ দিয়ে জ্বলন্ত প্লাজমা ছুঁড়ে দিচ্ছে। শনির আকাশ এর আগে কখনো পেছনদিকে একটা সূর্যকে দেখতে পায়নি।
অবশেষে রাতের সমাপ্তির সাথে সাথে ডিসকভারির গতিও অনেক কমে এসেছে। এখন আর সৌরজগৎ ছেড়ে যাবার ভয় নেই, কিন্তু শনির অর্বিট ছাড়ার ঝুঁকি থাকে।
চৌদ্দদিন লাগবে জ্যাপেটাসের অর্বিটে স্থান করে নিতে। বাকী উপগ্রহগুলোর কক্ষপথ একে একে ফেলে সেখানে যেতে হচ্ছে। তারপর মিলতেই হবে জ্যাপেটাসের সাথে। না পারলে ফিরে যাবে শনিতে, আটাশ দিনের কাজ শেষ করে আবার উঠে আসবে। এমনি কথা ছিল।
কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না, পরের বার গ্রহটা থাকবে শনির পেছনে।
ডিসকভারি ঠিকই তার সাথে দেখা করবে, কিন্তু সাক্ষী হিসেবে বোম্যান নাও থাকতে পারে, কারণ এ অবস্থা ফিরে আসতে কয়েক বছর সময়ের দরকার।
অধ্যায় ৩৫. জ্যাপেটাসের নয়ন
প্রথমবার জ্যাপেটাসকে দেখার সময় সে আধো আলো-ছায়াতে ছিল। এবার ভালমতো দেখা যায়, কারণ সে তার উনআশি দিনের কক্ষপথে এখন সবচে ঝলমলে দিন পোহাচ্ছে।
বোম্যান একটা কথা বলেনি মিশন কন্ট্রোলকে, কিন্তু নিজেকে নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে। অবশ্যই, একটু হলেও ডিশনে ভুগছে, মিথ্যা দৃশ্য-মিথ্যা স্মৃতি দেখছে।
যেমন এখন তার মনে হয় পুরো জ্যাপেটাসের পিছনদিকটাই তার দিকে চেয়ে থাকা পাঁপড়িবিহীন এক রাক্ষুসে চোখ। যেন সে গভীর আগ্রহে ছোট্ট ডেভ বোম্যানকে দেখছে। পনের হাজার মাইল দূর থেকে সে চোখের মনিটাও খুঁজে বের করে ফেলে। ছোট্ট, কালো সেই জিনিস এটা।
শেষবারের মতো ডিসকভারির জেটগুলো শনির বুকে পোড়া অণু-পরমাণুর হক্কা বইয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে নিজের চিরকালীন আবাসে। কেমন একটু গর্ববোধ করে বোম্যান-সাথে একটু কষ্টও পায়। এই অসাধারণ ইঞ্জিনগুলো অসম্ভব কাজ করেছে। ডিসকভারিকে পৃথিবী থেকে চাঁদ, চাঁদ থেকে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি থেকে নিয়ে এসেছে শনিতে; এই তাদের শেষ কাজ। নিজের প্রপেল্যান্ট ট্যাঙ্কগুলো খালি করলে আর সব মহাজাগতিক বস্তুর মতোই সে এক সামান্য উল্কা হয়ে মহাকাশে অভিকর্ষের দাসানুদাস বনে যাবে। উদ্ধারশিপটা তার জন্য কোনো বাড়তি জ্বালানিও আনতে পারবে না।
উপগ্রহ এগিয়ে আসার সাথে সাথে ফুয়েল গজও দ্রুত শূন্যের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে, বোম্যানের চোখ নেচে যাচ্ছে এসব ডিসপ্লের উপর। সে যদি কয়েক পাউন্ড ফুয়েলের অভাবে কাজ না সারতে পারে তো আর দেখতে হবে না…
ফুয়েলের গর্জন পড়ে যায়, ডিসকভারিও নিজেকে অর্বিটে সামলে নেয়। আরো জ্বালানী বাকী আছে। সারাক্ষণ সে জ্যাপেটাসকে পিচ্চি এক উপগ্রহ ভেবে এসেছে, এবার সামনে থেকে তাকে মোটেও পিচ্চি মনে হচ্ছে না। যেন যে কোনো মুহূর্তে ডিসকভারিকে গুড়ো করে ফেলতে উদ্যত এক মহাজাগতিক হাতুড়ি এই উপগ্রহটা।
এত ধীরে সে এগিয়ে আসে যে ব্যাপারটা বোঝা যায় না। তারপর কখন যেন বোম্যান মাত্র অর্ধশত মাইল নিচে এক অনন্য সৃষ্টিকে দেখতে পায়।
বিশ্বস্ত ছোট জেটগুলো তাদের শেষ শব্দ করেই ডিসকভারিকে পৌঁছে দেয় ঠিক ঠিক অর্বিটে। সে এখন ঘন্টায় আটশো মাইল গতিতে প্রতি তিন ঘণ্টায় চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে জ্যাপেটাসকে।
ডিসকভারি এখন আর কোনো স্পেসশিপের নাম নয়, এক স্যাটেলাইটের নাম।
অধ্যায় ৩৬. বিগ ব্রাদার
‘আমি আবারো দিনের পাশে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। সেই আগের রিপোর্ট করতে হবে আবারও। উপরিতলে মাত্র দু-ধরনের জিনিস চোখে পড়ে, একটা সেই কালো এলাকা-একদম কয়লা… রাতের দিক…অন্যটা নিচের ডিম্বাকার এলাকা…
‘চওড়া এলাকার ব্যাপারে এখনো কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। চারপাশ একেবারে মসৃণ, কোনো দাগটাগ বা আর কিছু চোখে পড়ে না। একেবারে সমতল আর…তরলও হতে পারে। তোমরা ছবি দেখে কী মাথামুণ্ডু বুঝবে তা বলতে পারি না, তবে আমার চোখে এ এক জমাট দুধসাগর।
‘এ জিনিসটা কোনো ভারি গ্যাসও হতে পারে…না, অসম্ভব মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে ধাঁধায় পড়ে যাই। এক আধটু জায়গা বদলায় মনে হয়। কিন্তু শিওর হয়ে কিছুই বলতে পারছি না…
‘…নিজের তৃতীয় অর্বিটে আবার আমি সেই সাদা জায়গার উপর এসে পড়েছি। গতবার ঠিক কেন্দ্রে যে মাপটা নিয়েছিলাম সেটা এবার পরীক্ষা করব। আমার আন্দাজ ঠিক হলে এর পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে আমি যাচ্ছিই…এটা যাই হোক না কেন।
‘…ইয়েস! সামনে একটা কিছু দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেখানে আমি আন্দাজ করেছিলাম সেখানে। উঠে আসছে! এক মিনিট, টেলিস্কোপটা সরিয়ে নিই…
‘হ্যাল্লো! কোনো ধরনের বিল্ডিং হবে বোধহয়। এক্কেবারে কালো, দেখাই যায় না। কোনো দরজা-জানালা নেই। খালি একটা বিরাট উঁচু স্ল্যাব-এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে কমসে কম এক মাইল উঁচু হবে। এটা দেখেই আমার মনে পড়ে গেল… অবশ্যই, কেন নয়? এ তো দেখতে ঠিক তোমাদের চাঁদের জিনিসের মতোই! এটা হল টি এম এ-ওয়ানের বিগ ব্রাদার!’
অধ্যায় ৩৭. অজি শ্রাবণের আমন্ত্রণে দুয়ার কাঁপে
একে নক্ষত্র দুয়ার বলা যায়।
ও ত্রিশ লাখ বছর ধরে আজকের দিনের প্রতীক্ষায় ছিল। এ কাজে একটা উপগ্রহ ধ্বংস করা হয়েছে, তার চিহ্ন আজো ভেসে বেড়ায় শনির চারপাশে।
সেই দীর্ঘ প্রহরের যবনিকা এবার পড়ে গেছে। আরো এক গ্রহে উন্নত জীবনের উন্মেষ ঘটেছে, এর প্রাণীরা নাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে চলে এসেছে এতদূর।
এক পুরনো, অতি পুরনো পরীক্ষা এবার নিজের ফলাফল দেখতে পাবে।
অনেক অনেক আগে যারা এ পরীক্ষণ শুরু করেছিল তারা মানুষ ছিল না, তাদের আকৃতি মানুষ থেকে অনেক অনেক দূরে। নিজেদের রক্তমাংসের শরীর নিয়ে বিহ্বল চোখে দূর দিগন্তে তাকালে তারা একাকী বোধ করে, ভর করে কীসের যেন হতাশা, কোত্থেকে যেন দুঃখ এসে জাপটে নেয়। শক্তি অর্জনের সাথে সাথে তারা অনন্ত নক্ষত্রবীথির দিকে ছুটতে শুরু করে অমিত তেজে।
তাদের অভিযানে কত ধরনের জীবন যে চোখে পড়ল! কত অযুত গ্রহের নিযুত প্রাণীর অগুণতি বিবর্তন-পদ্ধতি যে তারা দেখল তার কোনো লেখাজোকা নেই। অন্ত বিহীন নক্ষত্ৰধুলার আলোয় একটু ফিকে হয়ে আসা অসীম মহাজাগতিক রাতে কত বিচিত্র বুদ্ধিমত্তার বিকাশ যে তারা দেখল একমুহূর্তের তারার মতো জ্বলে উঠতে, কত তারাকে দেখল নিভতে!
এবং, যেহেতু সব গ্যালাক্সি চষে ফেলেও মনের চেয়ে দামী কোনো কিছুর সন্ধান তারা পায়নি তাই এর অরুণোদয়কেই তারা সবখানে সবচে বেশি মূল্য দিল। তারা তারার জগতের চাষী, তারা চাষ করে, বোনে, মাঝে মাঝে ফসলও তোলে।
কখনো কখনো হতাশ হয়ে উপড়ে ফেলতে হয় আগাছা।
হাজার হাজার বছরের মহাকাশ অভিযান শেষে তারা যখন পৃথিবীর বুকে পা রাখে তখন ডাইনোসররা বিলুপ্ত এক প্রাণী। জমে থাকা বাইরের গ্রহগুলোর পাশ দিয়ে উড়ে এসে মঙ্গলের মৃতপ্রায় মরুভূমির উপর একটু থামে, তারপর অপার আগ্রহ নিয়ে তাকায় পৃথিবীর দিকে।
নিচে ছড়িয়ে পড়েই অভিযাত্রীরা এক জীবন সাগর দেখতে পায়। বছরের পর বছর ধরে তারা পর্যবেক্ষণ করে, সংগ্রহ করে, শ্রেণীবদ্ধ করে সবকিছুর নাম। জানার মতো সব তথ্য পাবার পর পরিবর্তনে হাত দেয়। বহু প্রাণীর জীবন নিয়ে একটু চেষ্টা করে-তা ভূমিতে হোক আর সাগরে। কিন্তু পরীক্ষা সফল হল কি হল না তা জানতে আরো দশ লক্ষ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে যাবে।
তাদের ধৈর্য ছিল, কিন্তু তারা তখনো অমর নয়। ইউনিভার্সের দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের দশ হাজার কোটি সৌরজগতে করার মতো অনেক অনেক অনেক কাজ বাকী। অন্য দুনিয়া ডাকছে। সুতরাং আবার শূন্যতায় ভেসে পড়া তারা জানে-আর কোনোদিন পায়ের চিহ্ন এ পথে পড়বে না।
তার আর প্রয়োজন নেই। যে দাসদের ফেলে গেল তারাই বাকীটা সেরে ফেলবে।
পৃথিবীর যুগে বরফযুগ হাজারটা হিমবাহ নিয়ে এল, আবার ফিরে গেল; শুধু উপরের চাঁদে কোনো পরিবর্তন নেই। তার বুকে লুকানো আছে সবটুকু রহস্য। মেরুতে বরফ জন্মানোর চেয়েও ধীর গতিতে গ্যালাক্সি জুড়ে সভ্যতার জোয়ার উঠে এল, ভরে ভাসিয়ে দিল চারপাশ।
কত শত শত সাম্রাজ্য যে উঠে এল, কত সাম্রাজ্যের হল পতন তার ইয়ত্তা নেই। তারা শুধু বংশধরের জন্য জ্ঞানের সঞ্চয়টুকু রেখে হারিয়ে যায়। কখনোই পৃথিবীর কথা ভুলে যাওয়া হয়নি-কিন্তু তাতে কী, ফিরে আসা প্রশ্নাতীত। আরো লক্ষ লক্ষ নিরব দুনিয়ার মধ্যে এও এক। এদের মধ্যে কারো মুখে বুলি ফুটবে, কেউ কেউ স্তব্ধ থেকে যাবে চিরদিনের জন্য।
এবং এখন, আর সব নক্ষত্রলোকে বিবর্তনের এক নতুন জোয়ার শুরু হয়েছে। সেই অভিযাত্রীরা তাদের রূপ বদলে ফেলেছে মেশিনগুলো শরীরের চেয়ে বেশি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে। প্রথম প্রথম শুধু শরীর সেখানে জায়গা করে নিত, তারপর মস্তিষ্ক, তারপর শুধু চিন্তা। এবার তারা নক্ষত্রলোকে ঠিকমতো ঘুরে বেড়াতে পারল। তারা আর স্পেসশিপ বানায় না। তারা নিজেরাই স্পেসশিপ।
কিন্তু মেশিন-প্রাণীদের যুগ খুব দ্রুত ফুরিয়ে গেল। ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সাথে লাখো বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা স্বয়ং স্পেসের গায়ে জ্ঞানকে বন্দী করে রাখতে শিখল। জ্ঞানকে তারা অসীম ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আলোর জমাট ফটিকে লুকিয়ে রাখতে জানে। এবার তারা রেডিয়েশনের সৃষ্টি, অবশেষে বস্তুর নাগপাশ থেকে অনমুক্তি পাওয়া গেল।
কিন্তু রেডিয়েশন তথা তেজস্ক্রিয়তায়ও নাক সিঁটকানো থামে না। এরও একটু সীমাবদ্ধতা আছে। কণা নির্ভর ও পরীক্ষারত বস্তুর জন্য ক্ষতিকর এ পথ ছেড়ে সেই মুক্তিটাকে সত্যিকারের বাস্তবতা দেয়ার আশায় এবার তারা বিশুদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাদের ছেড়ে আসা খোলসগুলো মৃত্যুশীতলতা নিয়ে নেচে বেড়ায় হাজার হাজার বিশ্বে।
এখন তারা নিহারীকার ভাগ্যবিধাতা, সময় আর তাদের ছুঁতে পারে না। তারা এখন সব নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে চলতে জানে, মহাশূন্যের যে কোনো অতল সমুদ্রে শক্তির গাঢ় কুয়াশা হয়ে মিশে যেতে পারে।
কিন্তু আজো তারা তাদের পূর্বপুরুষদের শুরু করা পরীক্ষণের পথ ছেড়ে দেয়নি।
মহাশূন্যের চাষীরা এখনো রোপণ করা চারার পরিণতি দেখে।
অধ্যায় ৩৮. প্রহরী
‘শিপের পরিবেশ একেবারে বদলে যাচ্ছে। বেশিরভাগ সময় আমাকে একটা মাথাব্যথা নিয়ে থাকতে হয়। সব সময় অক্সিজেন পরিশোধন কাজ চললেও দৃষিতটা একেবারে সরিয়ে দেয়া যায় না। মাঝেমধ্যেই আমাকে পোড থেকে অক্সিজেন নিয়ে আসতে হচ্ছে…
‘আমি কোনো সাড়াই পাচ্ছি না টি এম এ-টু থেকে। তোমরা যে নাম দিয়েছ তার মর্মও সে রাখছে না। কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র নেই।
‘ডিসকভারি ষাট মাইলের চেয়ে বেশি কাছে যায় না। আমি ত্রিশ দিনের মধ্যে অভিযান চালাতে চাচ্ছি, কিন্তু তখন জিনিসটা অন্ধকারে চলে যাবে।
‘এমনকি এ মুহূর্তেও জিনিসটা আলো আর আঁধারের মাঝখানে। খুব বিরক্তিকর এর অবস্থা। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কদ্দিন এমন সাড়া ছাড়া থাকা যায়?
‘সুতরাং, আমি তোমাদের অনুমতি চাই। পোডটার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। জিনিসটাকে একেবারে কাছ থেকে দেখে আসব। দেখেশুনে ভাল মনে হলে পাশে কিংবা উপরে ল্যান্ড করতে পারি।
‘শিপ আমার উপরেই থাকবে নামার সময়, তাই নব্বই মিনিটের বেশি বাইরে থাকছি না।
‘তোমরা যাই বলনা কেন, আমি জানি এছাড়া আর কিছু করার নেই। শত কোটি মাইল এসেছি-ষাট মাইলের জন্য থেমে থাকতে পারি না।
.
সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে নক্ষত্রলোকের প্রবেশদ্বার সেই শিপটাকে দেখছে। এর স্রষ্টারা একে হাজারো কাজের জন্য বানিয়েছে-এটি সেসব কাজের মধ্যে অন্যতম। এটা বুঝতে পারে সৌর জগতের উষ্ণতা ছেড়ে এদুর আসার মানে।
এটা জীবিত হলে রোমাঞ্চ অনুভব করত। কিন্তু তার সে অনুভূতির প্রশ্নও ওঠে না। সে অপেক্ষা করছে ত্রিশ লাখ বছর ধরে, তার অপেক্ষার দৈর্ঘ্য অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত।
তাই শুধু দেখে, কোনো সাড়া দেয় না। একটু তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়া পেয়ে বোঝার চেষ্টা করে উৎসকে।
শিপ নিচে নেমে এসেছে। বারবার নিজের রেডিও বিস্ফোরণের সুরে কথা বলছে। এক থেকে এগারো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো আউড়ে যাচ্ছে ইচ্ছামতো।
এবার আরো হাজারো পথে লাখো ইশারা আসে। এক্স-রে, অতিবেগুনী রশ্মি, অবলোহিত…
নক্ষত্রদ্বার কোনো শব্দ করে না। এর বলার কিছুই নেই।
একটা বিশাল বস্তুকে নেমে পড়তে দেখে এটা সাথে সাথে সব হিসাব কষে ফেলে। লজিক ইউনিট তল্লাশী চালিয়ে জানতে পারে করণীয়। অনেক অনেক আগেই এ সম্পর্কে তথ্য দেয়া হয়েছিল।
শনির ঠাণ্ডা আলোয় তারকা জগতের প্রবেশমুখ তার ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলে।
ধীরে, অতি ধীরে, ত্রিশ লাখ বছর পর।
অধ্যায় ৩৯. চোখের ভেতর
ডিসকভারি শিপটাকে সে শেষবার আধ আকাশ জুড়ে থাকতে দেখল। তার চোখে সামান্য পরিবর্তন ধরা পড়ছে। মহাকাশযানটার বিভিন্ন হ্যাঁচ, সংযোগ, বিভিন্ন ধরনের প্লাগ আর যন্ত্রাংশকে সে চিনতে চেষ্টা করে। সূর্যালোকে স্নাত হয়ে এত লম্বা পথ পরিক্রমা শেষে এখানে আসায় শিপটা বোধহয় ম্লান হয়ে গেছে।
সূর্য এখন আর সব নক্ষত্র থেকে একটু বেশি উজ্জ্বল, এই যা। যে কেউ এর দিকে খোলা চোখে তাকাতে পারে। বোম্যান জানালার সামনে হাত পেতে দিয়েও সূর্যের উত্তাপ পায় না।
সে এবার বেরিয়ে যাচ্ছে, হয়তো শেষবারের মতোই। তার এই ধাতব বাড়িটা নিজের কাজ করতেই থাকবে, বোম্যান ফিরে আসুক আর না আসুক।
আর সে যদি ফিরে আসে তাহলে আরো বেশ কয়েক মাস বেঁচে থাকবে সজ্ঞানে। হাইবারনেশনের দেখভালের জন্য কোনো কম্পিউটার না থাকায় তার বাঁচার আশা ফুরিয়ে যাচ্ছে। ডিসকভারি টু আসবে চার পাঁচ বছর পর।
সে এসব ভাবনাকে প্রশ্রয় দেয় না। সামনে শনির উজ্জ্বল সোনালী গোলার্ধ ভেসে আছে। পুরো ইতিহাসে সেই এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য অর্জনকারী একমাত্র মানুষ।
সেই শনি রিংগুলোর প্রান্তে টাইটানকে এক উজ্জ্বল তারার মতো দেখাচ্ছে, বাকী উপগ্রহগুলো ম্লান। এই শতাব্দীর অর্ধেকটা কেটে যাবার আগেই মানুষ হয়তো এই সবগুলোতেই পা ফেলবে, কোন্ রহস্যের চাদর উঠে গেল তা জানার জন্য শুধু সে-ই বেঁচে থাকবে না।
অন্ধ সাদা চোখের তীক্ষ্ণ প্রান্ত ওর দিকে এগিয়ে আসছে। তার একটাই আশা, কথাগুলো যেন সব সময় দেড় আলোকঘণ্টা দূরের পৃথিবীতে চলে যায়। একবার নিরবতায় হারিয়ে গেলে মানুষ কোনোদিনই তার পরিণতির কথা জানবে না।
বহু উপরের কালো আকাশে ডিসকভারি এখন এক তারা হয়ে জ্বলছে। ত্বরণ কমানোর জন্য পোডের ঘোঁট জেটগুলো কাজ শুরু করবে, এগিয়ে আসবে, চির রহস্যের দেশ, শুধু চোখের সামনে থেকে উবে যাবে ডিসকভারি; এতদিনের সাথীকে সে আর খালি চোখে দেখতে পাবে না।
ত্বরণ বেশি হয়ে গেলে আবার অনেক বেশি ফুয়েল খরচ হবে গতিটা কমিয়ে আনতে। কিন্তু এখানে পুরো পোডের ওজন হবে মাত্র কয়েক পাউন্ড; তাই সে সহজেই মানিয়ে নেবে। আর না হলেও কিছু যায় আসে না। এখানে, পোডের ভিতর বা উপগ্রহের উপরে দু-একমাস আগে মৃত্যুবরণ করা আর সেখানে বেশি বাঁচায় তেমন কোনো ফারাক নেই…
নিচের সাদা সমতলের উপর স্থির দাঁড়িয়ে আছে কালো স্তম্ভটা কী এক অজানা অহংকার বুকে নিয়ে। সে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে আছে এখন। দেখেশুনে মনে হচ্ছে এর উচ্চতা কমবেশি দু-হাজার ফুট হবে। গায়ের অনুপাতও সেই ১:৪:৯।
‘আমি এখন মাত্র তিন মাইল দূরে। চার হাজার ফুট উপরে অ্যাটিচ্যুড কন্ট্রোল জেট চেপে ধরব। এখনো বিন্দুমাত্র বৈচিত্র্য নেই। নেই কোনো সাড়া। এত বছর পর তোমরা এক-আধটু উল্কাটুল্কার ক্ষয়ক্ষতিও আশা করতে পার, তাও নেই। একেবারে মসৃণ!
‘ছাদের উপর কোনো টুকরো পড়ে নেই। কোনো খোলা-বন্ধের ব্যাপারও চোখে পড়ছে না। আশা করছি সেখানে ঢোকার কোনো…
‘এখন আমি ঠিক পাঁচশ ফুট উপরে ভাসছি। ডিসকভারি সরে যাবার আগেই আমাকে ফিরতে হবে। উপরেই ল্যান্ড করব। আশা করি সাথে সাথে আমাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে না।
‘এক মিনিট… ব্যাপারটা বেখাপ্পা…’
আর কোনো শব্দ নেই। সে কী দেখল তার বর্ণনা দেয়ার সময়ই পায়নি। জিনিসটাকে অন্যরকম লাগছিল কিন্তু সেটা সে বুঝতেও পারেনি। চোখের ভুল হতে পারে…যেন ওটা সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। যেন ভিতরের দিকটা বাইরে আর বাইরের দিক ভিতরে চলে আসছে…কিংবা উপর থেকে চোরাবালি চলে যাচ্ছে নিচের দিকে…।
ঠিক এ ব্যাপারটাই ঘটছিল সেখানে। এটা আরো বিশাল, স্থির কোনো স্তম্ভ নেই। অসম্ভব, অবাস্তব, অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাই চোখের সামনে ঘটে গেল। যাকে ছাদ মনে হচ্ছিল সেই চলে গেছে কোন্ অতল গর্ভে। তার শেষ নেই। যেন কোনো অন্ত বিহীন পথে প্রবেশ করছে সে…
জ্যাপেটাসের নয়ন এবার জীবন পেয়েছে, পলক ফেলেছে অনেক অনেক বছর পর।
ডেভিড বোম্যান একটা মাত্র ভাঙা বাক্য বলার সুযোগ পেল নয়শো মিলিয়ন মাইল দূরের মিশন কন্ট্রোলের মানুষদের কাছে যেটা যুগ-যুগান্ত ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে:
‘জিনিসটা ফাঁপা-এর কোনো অন্ত নেই-আর-ওহ মাই গড! এটা তারায় তারায় ভরা!…
অধ্যায় ৪০. তোমার দেখা পাব বলে …
নক্ষত্ৰদ্বার খুলে গেল।
বন্ধ হলো নক্ষত্ৰদ্বার।
এক অতি ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে আবার স্থানটা ঠিক হয়ে গেল; আগের মতো।
আরো একবার জ্যাপেটাস বিরাণভূমিতে পরিণত হয়েছে। ত্রিশ লাখ বছর পর প্রাণের ছোঁয়া পেয়ে আবার উপগ্রহটা একাকিত্বের যন্ত্রণা ভোগ করবে।
কিন্তু উপরে এক সাথী আছে তার। ডিসকভারি এখনো ঠিক পরিত্যক্ত হয়ে পড়েনি। সে তার প্রভুর খবর পৌঁছে দিচ্ছিল বিজন প্রান্তর ভেদ করে আরেক কোণে।
এ সংবাদ না করবে কেউ বিশ্বাস, না পারবে বুঝতে।
৬. নক্ষত্রের প্রবেশদ্বার
ষষ্ঠ পর্ব : নক্ষত্রের প্রবেশদ্বার
অধ্যায় ৪১. মহাকেন্দ্র
গতির কোনো অনুভূতি ছিল না কিন্তু সে সেই অসম্ভব তারার রাজ্যে পড়ে যাচ্ছিল যেগুলো উপগ্রহের কালো বুকে জ্বলছে অবিরত। না-ঠিক সেখানে ওরা ছিল না। সে বুঝতে পারে। সে হতাশভাবে ভাবে, আগেই হাইপারস্পেস আর ট্রান্সডাইমেনশনাল ডাক্ট থিওরিতে বিশ্বাস করা উচিত ছিল।
কিন্তু আর সব শতকোটি মানুষের কাছে সেটা থিওরি হলেও ডেভিড বোম্যানের কাছে নয়।
সম্ভবত ছাদটার ছাদছাদ ভাবই আসলে দৃষ্টিভ্রম, এর কোনো তল নেই। কিংবা উপরিতল আছে, সেটা মিলিয়ে গেছে তাকে ভেতরে নেয়ার জন্য। কিন্তু ঠিক কোথায় নেয়ার জন্য? এক বিরাট চৌকোণা গর্তের ভিতর সে সরাসরি পড়ছিল। গতি বাড়ছিল প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু তলাটা কখনোই এগিয়ে আসেনি।
শুধু তারকাগুলো সরে যাচ্ছিল তাদের ধারক ফ্রেম থেকে। প্রথম প্রথম সে বুঝতেই পারেনি তাদের সরে যাওয়ার ব্যাপারটা। কিন্তু পরেই আসল দৃশ্য চোখে পড়ে। ছড়িয়ে পড়ছে নক্ষত্রলোক, ধেয়ে আসছে তার দিকে! কেন্দ্রের দিকের তারাগুলোকে তেমন নড়তে দেখা যায় না, পরিধির দিকেরগুলো গতিবৃদ্ধি করেই চলেছে। তারপর তারা আলোর রেখার মতো বিলীন হয়ে যায়। তার মানে উঠে আসছে জগৎটা। কেমন জগৎ এটা? কেমন জগৎ!
যেন অসীম কোনো উৎসের দিকে এই যাওয়া। মাঝখানটায় যাওয়ার পালা শেষ হবে কিনা বোঝা যায় না। সে কোনো সূর্যের বুকে পড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কি এই ব্যাপার হতেই থাকবে? কিন্তু তারা কেউ সামনে আসে না। সবাই একটা বিরাট দূরত্ব রেখে সরে যায় সেই অনন্ত কালো ফ্রেমের গায়ে। উঠে আসে আরো।
এখনো শেষপ্রান্ত এগিয়ে আসেনি। মনে হয় যেন দেয়ালগুলোও তার সাথে সাথে চলেছে। কিন্তু ত্বরণ অনুভব করবে না এ কেমন কথা! নাকি সে সত্যি সত্যি স্থিরই আছে, চারদিকে ছুটে চলছে মহাকালের মহাকাশ…
শুধু স্পেস নয়, এবার সে বোঝে তার সাথে কী হচ্ছে। পোডের ইট্রুমেন্ট প্যানেলের ছোট্ট ঘড়িটিও এবার পাগলামি শুরু করে দেয়।
সাধারণত সেকেন্ডের দশভাগের একভাগ দেখানো সংখ্যাগুলো দেখে বোঝ যাবার আগেই হাওয়া হয়ে যায়। এখন সে ভালভাবেই সেগুলোকে পড়তে পারছে। শেষে সময় গণক থেমে গেল সেকেন্ডের দশভাগের পাঁচ আর ছয়ের মধ্যে। ক্লান্ত সময় তার অবিরাম চলা বন্ধ করে দিয়েছে!
সে দেখতে পাচ্ছে, ঠিকমতো বুঝছে সব, এখনো চারপাশে দেয়াল। সে দেয়ালের গতি শূন্যও হতে পারে, আবার আলোর চেয়ে লাখগুণ বেশিও হতে পারে। কেন যেন সে একবিন্দুও আশ্চর্য হলো না। মনে কেন যেন একটুও ভয় নেই। উল্টো অবাক করা শান্ত ভাব ঘিরে ধরেছে তাকে। একবার তাকে স্পেস মেডিকরা হ্যালুসিলেশন ড্রাগ দিয়ে পরীক্ষা করেছিল। সে হঠাৎই বুঝছে, তার চারপাশটা অবাক করা, তাতে কী-ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
একটা রহস্যের আশায় সে শত কোটি মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছে, সে রহস্য এবার হাজির হবে সামনে।
সামনের চৌকোণাটা আলোময়। উজ্জ্বল তারাগুলো একটা দুধ-সাগরে মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন স্পেস পোড কোনো অদৃশ্য সূর্যের আলোয় আলোকিত কুয়াশা-মেঘের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।
এবার সে টানেল ছেড়ে যাবে। কিন্তু দূরপ্রান্ত এখনো এগিয়ে আসেনি। তারপর একসময় এগিয়ে আসে, ছড়িয়ে পড়ে তার সামনে।
হঠাৎ মনে হল সে উপরে উঠছে। সে কি জ্যাপেটাসের অন্য প্রান্ত ধরে উঠে আসছে? মুহূর্তেই বাতিল হয়ে যায় ধারণাটা। এর সাথে জ্যাপেটাস বা মানবীয় হিসাব নিকাশ বা সৌরজগতের কোনো সম্পর্ক নেই।
কোনো বায়ুমণ্ডল না থাকায় সে অবিশ্বাস্য নিচের দৃশ্যও দেখছে পরিষ্কার। ওটা একেবারে সমতল! সে নিশ্চয়ই এক অকল্পনীয় রকমের বড় ভুবনের উপর ভাসছে। নিচে দেখতে পেল অনেক অনেক সূক্ষ্ম দাগ, সেগুলো নিশ্চয়ই মাইলের পর মাইল এলাকাজুড়ে আছে। যেন কোনো পাগলাটে মহাকাশের খেলুড়ে ত্রিকোণ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ এসব এঁকে খুব মজা পেয়েছে কোনোদিন। বোম্যান কয়েকটা এলাকার মাঝখানে কালো কালে কী যেন দেখতে পায়। ভালমতো খেয়াল করে সবগুলোর ভিতরেই একটা করে টি এম এ’র অস্তিত্ব দেখতে পায় সে।
উপরের আকাশ আরো অদ্ভুতুড়ে আকার নিয়েছে, নিচের অসীম সমতলের চেয়েও বিস্তৃত তর হাল। সেখানে কোনো তারা নেই, মহাকাশের চিরাচরিত অন্ধকার নেই। আছে শুধু হাল্কা দ্যুতির দুধসাদা অসীম এক আকাশ।
বোম্যান একবার অ্যান্টার্কটিকের এক বর্ণনা শুনেছিল। পিংপং বলের মতো চারদিক সাদা আর সাদা। কথাটা নিশ্চয়ই সেখানে না মানিয়ে এখানে মানিয়ে যায়। এখানকার সাদার পেছনে কোনো মহাজাগতিক বস্তুগত কারণ নেই। এ হল আসল বায়ুশূন্যতা।
এবার তার সচেতনতা অন্যদিকে চলে যায়। জায়গাটা পুরোপুরি খালি নয়! উপরে, অকল্পনীয় উপরে ছোট ছোট কালো বিন্দু চোখে পড়ে। সেগুলো কী?
বোম্যান একজন জ্যোতির্বিদ। স্থানটা চিনে নিতে তার তাই তেমন সমস্যা হয় না।
সেই কালো বিন্দুগুলোই সাদা নক্ষত্র ছিল, আর দুধসাদা স্পেস ছিল কালো। সে গ্যালাক্সি মিল্কি ওয়ের ছবির উল্টা দৃশ্যটা দেখছে!
খোদার দোহাই! আমি কোথায়! নিজেকে প্রশ্ন করে বোম্যান। প্রশ্ন করেই হঠাৎ সে বুঝে ফেলে আর কোনোদিন সে উত্তরটা জানতে পারবে না। দেখে মনে হচ্ছে পুরো মহাবিশ্ব…পুরো ইউনিভার্সকে উল্টে দেয়া হয়েছে, টেনে বাইরের দিককে ভিতরে আর ভিতরের দিকে বাইরে এনে ফেলা হয়েছে। এ স্থান মানুষের জন্য নয়।
ক্যাপসুলটা যথেষ্ট গরম হলেও ডেভ বোম্যান কাঁপতে শুরু করে থরথরিয়ে। বন্ধ করতে চায় নিজের চোখ, অস্বীকার করে চারপাশের অনিশ্চয়তাকে। কিন্তু কাজটা কাপুরুষতা। সে চোখ বন্ধ করবে না। সে দেখবে। শেষ পর্যন্ত দেখবে।
জগত্তা ধীরে ধীরে তার নিচে ঘুরে উঠল। কিন্তু দৃশ্যপটে কোনো পরিবর্তন আসেনি। অনুমানে ধরে নেয় এখন সে সারফেসের দশ মাইল উপরে আছে। হাজার চেষ্টা করেও জীবনের কোনো চিহ্ন বের করতে পারেনি। বুদ্ধিমত্তা এখানে এসেছিল। নিজের ইচ্ছামতো কাজ করিয়েছে। তারপর চলে গেছে কাজ শেষে।
হঠাই প্রায় বিশ মাইল দূরে উপরে আরেকটা জিনিস ভাসতে দেখল। তাকাতে তাকাতেই সেটা চলে গেল দূরে। সিলিন্ডারের মতো লম্বাটে জিনিসটা হাজারো ধাতব কাঠামোর একটা সমন্বয়। কোনো কমলালেবুকে ছিলে ফেললে যেমন হয় তেমন করেই এর বাইরের পুরো দেয়াল আর আবরণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কত হাজার বছর ধরে শূণ্য মহাকাশযানটা ঘুরতে ঘুরতে এ অবস্থায় পড়েছে কে জানে! আর কারা সেই প্রাণী!
এমন সময় সে পরিত্যক্ত জিনিসটার কথা ভুলে গেল সামনে আরো একটা কিছু আসতে দেখে।
প্রথমে জিনিসটাকে সমতল চাকতির মতো লেগেছিল, পরে বুঝতে পারে সেটা সরাসরি তার দিকে আসাতেই এমন দেখা যায়। কাছে এসে পাশ কাটিয়ে গেলে সে বুঝতে পারে যে জিনিসটা লাটিমের মতো আর কয়েকশো ফুট লম্বা। এও বোধহয় কোনো শিপ। ঘুরতে ঘুরতে এগোয় বলে তেমন কিছু বোঝা যায়নি।
জিনিসটা অনেক দূরে চলে যাবার আগ পর্যন্ত সে চোখ ফেরাতে পারে না। তারপর বুঝতে পারে যদি তার চোখ ঠিক দেখে থাকে তো এর স্রষ্টারা মানুষের পরিচিত একটা ব্যাপারের সাথে মিল রেখেছে। তাদের জাহাজ বানানোর উপাদানটা পরিচিত হলেও সহজলভ্য নয়। স্বর্ণ।
বোম্যান আবারো তাকায় রিয়ারভিউ মিররে। সেটা তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে চলে গেছে। সে তো উপেক্ষা করতে পারে না। নিচের বিরাট গ্রহের লক্ষ প্রবেশপথের কোনো একটা দিয়ে শিপটা ঢুকে গেল ভিতরে। আর কেউ নেই। এবার একাকীত্বটা বড় বেশি বাজছে বোম্যানের অন্তরে।
একটু পর নিজেও নামতে শুরু করে উপরিতলের দিকে। এখনো আরেক চতুষ্কোণী খাদক হাঁ করে আছে। খালি আকাশ বন্ধ হয়ে গেল, বিশ্রাম নেয়া শুরু করল ঘড়ি, এবং আবারো পোডটা অসীম কোনো গহ্বরের সন্ধানে নেমে পড়ল চৌকোণা পথে।
কিন্তু এবার সে নিশ্চিত যে আর ফেরা হচ্ছে না সৌরজগতে। কিন্তু এখন তার বোধ স্মৃতিকাতরতার অতীতে চলে গেছে। কারণ সে এমন কিছুর খোঁজ পেয়ে গেছে যার পর আর পাওয়ার কিছু বাকী থাকে না।
হায়, মানুষ জানতে পারল না। সে মানুষকে কথাটা জানাতে পারল না।
সৃষ্টি জগতের সব সৌরজগতেই একটা করে প্রবেশদ্বার আছে। সেই সব প্রবেশদ্বার একত্র হয়েছে এমন কোথাও যেখানে সময় থমকে দিয়ে পুরো গ্যালাক্সির প্রকৃতিকে পেছনদিকে টেনে রাখা হয়েছে। জানা থাকলে সেখান থেকে ইচ্ছামতো যেখানে খুশি যাওয়া যায়। কোটি কোটি আলোকবর্ষ পথ যেতে হলে পৃথিবী থেকে জ্যাপেটাসে আসতে হবে। জ্যাপেটাস থেকে এখানে, এখান থেকে লক্ষ্য সৌর জগতের প্রবেশদ্বারে, ব্যস। এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যেতে হলে মহাশূন্য এমনকি নিজের সৌরজগৎ পেরুনোরও কোনো দরকার নেই।
এ ‘স্থান’ হল পুরো গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় স্টেশন।
অধ্যায় ৪২. অচেনী আকাশ
অনেক সামনে, পথের শেষ প্রান্ত ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে আসে। তারপর ছোট্ট স্পেসপোড তার সামনে নতুন আকাশ দেখতে পায়।
সে আবার স্বাভাবিক স্পেসে ফিরে এসেছে। কিন্তু একটু চোখ বুলিয়েই বুঝে নিতে পারে যে এটা সে আকাশ নয়। এখান থেকে পৃথিবী কত শত আলোকবর্ষ দূরে তা কেউ বলতে পারবে না। সে তারার জগৎ ভালমতো চেনে। এই নক্ষত্রগুলোর কোনোটা কোনো মানুষ খালি চোখে দেখতে পায়নি।
বেশিরভাগ তারকাই দ্যুতিময় আলোর মালায় গাঁথা। মাঝে মাঝে মহাজাগতিক ধুলো শুধু সে পথকে অদৃশ্য করে দিয়েছে। দেখতে মিল্কি ওয়ের মতোই কিন্তু অনেক অনেক উজ্জ্বল। তার মানে সে গ্যালাক্সির সেই বিজন প্রান্তর থেকে ঘন কোনো এলাকায় চলে এসেছে। সৌরজগত গ্যালাক্সির প্রান্তসীমায় অবস্থিত। এতটাই প্রান্তে যে প্রায় পুরো গ্যালাক্সিটাকেই পৃথিবী থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব। সেখানে তারার দল আলাদা আলাদা আর অনেক দূরে দূরে বাস করে। সামনের আলোকমালাটা সম্ভবত গ্যালাক্সির কোনো বাহু।
সে আশা করে এটা মিল্কি ওয়ে। কারণ ঘর থেকে আরও দূরে চলে যেতে চায় না। একটু পরেই বুঝতে পারে ভাবনাটা শুধু বোকাটেই নয়, ছেলেমানুষী। সে এত দূরে চলে এসেছে যে এখানে এখন কোনো তারা বিস্ফোরিত হলে পৃথিবীর টেলিস্কোপে তা ধরা পড়বে কয়েক শতাব্দী পর। সহস্রাব্দও হতে পারে। এখানে থাকা আর অন্য কোনো গ্যালাক্সিতে চলে যাওয়ায় কোনো তফাৎ নেই।
সে পেছনে তাকায়। কোত্থেকে উদয় হল দেখতে হবে। এবার আরো একটা হোঁচট অপেক্ষা করছিল। পেছনে কোনো স্টেশন বা জ্যাপেটাসের মতো কোনো এলাকা নেই। শুধুই কালো আকাশের গায়ে তারার মেলা। তার মানে পৃথিবী থেকে অন্য জগতে যেতে হলে জ্যাপেটাসে না গেলেও চলবে। পৃথিবীর সামনেই কোনো পথ হাজির হতে পারে, আবার যেখানে যাবার কথা সেখানকার আকাশে উগড়ে দিতে পারে।
কিন্তু নতুন করে পুরোনো ভাবনা তাকে পেয়ে বসে। অচেনা আকাশে চেনা কিছুই নেই এখন। একটা নক্ষত্রদ্বার থাকলেও তাকে পরিচিত বলা যেত।
সামনে অত্যন্ত নিখুঁত একটা নক্ষত্র-গোলক। একক কোনো নক্ষত্র নয়, অসীম তারার দল। নক্ষত্রপুঞ্জ। এগিয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে। কেন্দ্রে আলো আর আলো, কোনো নক্ষত্রকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। বাইরের দিকটা হঠাৎ করে শেষ হয়ে যায়নি বরং হাল্কা হয়ে মিশে গেছে কালো আকাশের সাথে। আকৃতি এত বিশাল যে হাজারটা সৌরজগৎ এর ভিতরে ছেড়ে দিলে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে যাবে।
বোম্যান জানে এ মহামহিম অপার্থিব এবং অকল্পনীয় বিশাল আকৃতির চেয়েও বড় এলাকাটার নাম গ্লোবুলার ক্লাস্টার। সে আবারো এমন একটা কিছুর দিকে তাকিয়ে আছে যা আর কোনো মানুষের চোখ কোনোদিন দেখেনি। এমনকি সবচে শক্তিমান টেলিস্কোপেও এ দৃশ্য একেবারে অস্পষ্ট দেখা যাবে।
তার কোনো নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব মনে পড়ছে না, কিন্তু এটুকু মনে আছে যে পৃথিবীর সবচে কাছেরটাও কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।
কেমন করে যেন পোডটা আরো ভিতরে চলে গেল, সেখানে এক নতুন বিস্ময় ওৎ পেতে আছে। সামনে এক বিরাট লালচে নক্ষত্র। রেড জায়ান্ট স্টার। এর উজ্জ্বলতা এতই স্নান যে ভোলা চোখে তাকাতেও কোনো সমস্যা হয় না। এখান থেকে পৃথিবীর আকাশের চাঁদের চেয়েও বড় দেখাচ্ছে। এর দীপ্তিটা জ্বলন্ত কয়লার চেয়ে বেশি নয়। লালের গায়ে হলুদের চিকণ রেখা। সরু দাগগুলো যে হাজার মাইলের খরস্রোতা আগুন-নদী তা বোঝাই যায় না। ওরা মরতে বসা সূর্যের বুকে হারিয়ে যাবার আগে যথাসম্ভব চলাচল করে নিচ্ছে।
মৃতপ্রায় শব্দটা মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক থাকলেও সূর্যের ক্ষেত্রে যেন মানায় না। এ সূর্য তার যৌবনের অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে এসে দ্যুতি হারিয়ে বসেছে। তার জ্যোতির্ময় বেগুনী, নীল আর সবুজ বর্ণালীর শত শত কোটি বছরের যুগ শেষ করে শান্ত সৌম্য দীপ্ত রূপ নিয়েছে আরো অনাগত ভবিষ্যতের অপেক্ষায়। এবং বিগত সময়ের তুলনায় অনাগত সময় আরো আরো বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে আসবে। তার দুর্দম যৌবনের চেয়ে সৌম্য-তারুণ্য চলবে হাজারগুণ বেশি সময় ধরে।
এখন আর বোম্যান কোনো নিয়ন্ত্রণ অনুভব করছে না। কিন্তু সে জানে, যে শক্তি তাকে এখানে টেনে এনেছে সেটা তার বজ্রমুষ্ঠিকে একটুও শিথিল করেনি। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যেন তার সামনে হাস্যকর ও মূল্যহীন।
সে বোঝার চেষ্টা করছে কোনো অবশ্যম্ভাবী নিয়তি এবার তাকে টানবে। সম্ভবত এই সূর্যের কোনো কক্ষপথ ধরে কোনো গ্রহ ঘুরছে, সেখানে তাকে হয়তো নিয়ে যাওয়া হবে। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ সে সূর্যের প্রান্তসীমায় অবাক করা কিছু দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে যায়।
পেছনে, একটা সাদা জ্যোতির উদয় হয়েছে, এগিয়ে আসছে দ্রুত। উঠে আসছে এ সূর্যের দিকে। সেটাই কি সময় থেকে সময়ে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে ঘুরে বেড়ায়? পরে বুঝতে পারে, না। সেটাও এক নক্ষত্র, আকারে শুধু ছোট আর হাজারগুণ উজ্জ্বল।
সে নিজের ভাবনা দেখে নিজেই হেসে ওঠে। সূর্যোদয়ে সে বিমোহিত… সূর্যোদয়, একটা সূর্যের উপর!
নীলচে আলোর এক ছোট্ট গোলক সেটা। ছোট সূর্যটা খুব দ্রুত সঙ্গীর চারপাশে ঘুরে বেড়ায় মনে হচ্ছে। কিন্তু এই সূর্যের কি কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না? ভাবতে ভাবতেই সে দেখতে পায় প্রতিক্রিয়ার রূপ। ছোট দানবের শক্তির টানে কাবু হয়ে বড় নক্ষত্রের গা থেকে হাজার হাজার মাইল লম্বা আগুনের শিখা উঠে যাচ্ছে উপরদিকে। আগুনের জোয়ার!
সেই ছোট্টটা নিশ্চয়ই কোনো হোয়াইট ডোয়ার্ফ। এরা আকারে বড়জোর পৃথিবীর সমান, কিন্তু ভরে কোটিগুণ বড়। এমন বেখাপ্পা সৌর জুটি আসলে মোটেও বেখাপ্পা নয়। কিন্তু বোম্যান কোনোদিন এমন দৃশ্য দেখার বেখাপ্পা কল্পনা করেনি।
এরমধ্যেই সাদা বামন তার সাথীর অর্ধেকটা পার করে ফেলেছে। সম্ভবত কয়েক মিনিটে একবার পাক খায় পুরো এলাকাটা। অবশেষে বোম্যান বুঝতে পারে যে সেও ভেসে চলেছে। কারণ অন্তরালের এক ঝকঝকে নক্ষত্র এর মধ্যেই সামনে আসতে আসতে অনেকটা স্পষ্ট বস্তুতে পরিণত হয়েছে। নিশ্চয়ই এখানে সে যাচ্ছে।
কিন্তু সেটা কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ নয়।
সেটা এক ধাতব জিনিস। কৃত্রিম উপগ্রহের মতো এর নাম দেয়া যায় কৃত্রিম গ্রহ। বিশাল তার আকৃতি, সারফেসে বসে থাকা শহরের সমান একেকটা মেশিন দেখেও সে আঁতকে ওঠে। সে যতবার আঁতকে উঠেছে গত কয়েক মাসে ততবার বোধহয় কোনো মানুষ চমকায় না এক জীবনে।
বড়গুলোর প্রতিটির চারপাশে একরের পর একর এলাকাজুড়ে ছোট মেশিনের রাজত্ব। সেগুলোও সমান নয়। কোনো কোনোটা দেখা যায় না আবার কোনোটা চোখে ধাক্কা দেয়। সে এমন কয়েকটা এলাকা পেরুনোর পর বুঝতে পারে যে ছোট মেশিনগুলোর প্রতিটি অঞ্চল একেকটি মহাকাশ নৌবহর। আর গোলাকার ধাতব জিনিসটা আর কিছু নয়, মহাজাগতিক পার্কিং লট।
যেহেতু পুরো পরিবেশ এবং এর প্রতিটি অংশই তার অচেনা সেহেতু সে কিছুতেই আন্দাজ করতে পারল না নিচের দৃশ্যটা কত বড়। সেখানে কোনো মহাকাশ নৌবহরে ডিসকভারিকে ঢুকিয়ে দিয়ে উপরে উঠে এলে বোঝা যেত। নিচের ওগুলো কত বর্ণের, গোত্রের আর আকৃতির তা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। কোনোটা স্বচ্ছ, কোনোটা আলোকদাত্রী, কেউ লম্বা, কোনোটা পুরোপুরি চাকতির মতো, কোনোটা আকার বদলাচ্ছে স্থির থেকেই…মাথা খারাপ করা দৃশ্য।
এ নিশ্চয়ই কোনো মহাজাগতিক অর্থনৈতিক মিলনমেলা।
কিংবা মিলনমেলা ছিল কয়েক মিলিয়ন বছর আগে। কারণ জীবনের কোনো নিদর্শনই সে দেখতে পায়নি অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও। বরং মহাকালের হাজারো উল্কা নির্দ্বিধায় এর উপর পড়েছে বছরের পর বছর। এত বিশাল জিনিসটা কেন অকেজো পড়ে আছে তা আর সে জানে না। যা জানে তা হল সামনের ঐ ধাতব গড়নটা এখন শুধুই মহাজাগতিক আস্তাকুঁড়।
সে কত সহস্র বছরের ব্যবধানে এসেছে তাও জানে না। এই মহা সম্মেলন আর নির্মাতাদের দেখতে পেল না শুধু সময়ের ব্যবধানের জন্য। একটু আঁৎকে ওঠে সে কথাটা ভেবে। তার মন অপার্থিব বুদ্ধিমত্তার খোঁজে আঁকুপাকু করছিল এতদিন।
সে কোনো পুরনো ফাঁদে আটকা পড়ে যায়নিতো? লাখো বছর আগে স্টেশন গ্রহের যে গর্তে ও পড়ে যায় সেই পথ ধরে যারা যেত তারা হয়তো এখানেই নিজেদের নিয়ে আসতে চেষ্টা করত। সেই পথ একই কাজ করে যাচ্ছে আজো, তারাই শুধু নেই।
আর তার পর, আরো ভয়াবহ ধারণা খেলে গেল ডেভ বোম্যানের মাথায়। নাকি পথটা এখন শুধু নষ্ট স্পেসশিপ আর মহাকাশ জঞ্জাল নিয়ে আসে এখানে? আরো অনেক প্রাণীর মতো সেও কি বাতাসের অভাব পড়ার পর এই স্পেস পোডের ভিতর মারা পড়বে?
যাক, আরো আশা করাটা অবান্তর। এরই মধ্যে এমন শত ব্যাপার দেখে ফেলেছে যার যে কোনো একটা দেখার আশায় মানুষ নির্দ্বিধায় প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। তার মৃত বন্ধুদের কথাও মনে পড়ে। তাদের তুলনায় বোম্যানের আর কিছু চাওয়ার থাকে না।
জীবনের শেষ প্রান্ত নিয়ে ভাবার মুহূর্তেই চোখে পড়ে পোর্টটা এগিয়ে আসছে। তার দিকে, কিন্তু উপরে উঠছে না। একটু পর বিশাল ধাতব গোলক পেছনে পড়ে যায়, সামনে এগিয়ে চলে স্পেস পোড, আর তার ভিতর ডেভ বোম্যান।
যাক, তার ভাগ্যলিপি এখানে ফুরিয়ে যায়নি। বোম্যান ভাবে। এবং দেখতে পায় ভাগ্যলিপির শেষ অধ্যায়।
সেই ছোট্ট দানব সূর্য এবার এগিয়ে আসছে।
অধ্যায় ৪৩. জ্বলন্ত নরক
এখন সামনে শুধু লাল সূর্য। সেটা পুরো আকাশ জুড়ে বসে আছে। সে এত কাছে চলে এসেছে যে এদিক-ওদিক নড়তে থাকা আগুন নদী আর উন্মাতাল গ্যাসের ঝঞ্ঝা স্পষ্ট চোখে পড়ে। আর আগুনের হল্কাগুলো ধীরে উপরে উঠে আসছে। ধীরে? তার চোখে ব্যাপারটা পড়তে হলে ঘণ্টায় লক্ষ মাইলেরও বেশি গতি দরকার…
যে আগুনে নরকে সে পড়তে যাচ্ছে তার আকার নিয়ে সে চিন্তাও করে না। তার চিন্তাভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন? একটা সূর্যের বুকে কি কারো পড়া সম্ভব? লক্ষ মাইল দূর থেকেই সে স্রেফ হাওয়া হয়ে যাবে।
বৃহস্পতি আর শনির বিশালত্ব তার উপর টেক্কা মেরেছিল কোনো অজানা গিগামাইল দূরত্বের সৌর জগতে থাকাকালে। কিন্তু বৃহস্পতি এখানে থাকলে লজ্জায় মুখ লুকাতো।
আগুনের সমুদ্র পেছনে ছড়িয়ে পড়ায় তার আতঙ্কিত হওয়ার কথা, কিন্তু অবাক ব্যাপার-সে শুধু নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে। তার ভাবনার কিছু নেই, নিরাপত্তা দেয়ার জন্য তার পেছনে কোনো অদৃষ্ট নিয়ন্তা কাজ করছে। সে এখন সূর্যের এত কাছে যে তাপ আসুক চাই না আসুক, শুধু এতক্ষণের তেজস্ক্রিয়তায় জ্বলে পুড়ে তার খাক হয়ে যাবার কথা। কিন্তু কিছু হয়নি। অদৃশ্য কোনো বর্ম যে কে ধরে রেখেছে তা মৃত্যুর আগে জানতে পারলে বেশ হতো। আর এতক্ষণ ধরে যতটুকু ত্বরণ তার শরীর সহ্য করে এসেছে এমনটা সত্যি সত্যি ঘটলে অনু-পরমাণু একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কথা।
না, মরণ এত এগিয়ে আসেনি। এত কষ্ট তার জন্য করা হয়ে থাকলে সামনে আর কিছু থাক না থাক, আশা থাকে।
পোড এবার সূর্যের সারফেসের সমান্তরালে চলতে চলতে ধীরে নেমে যাচ্ছে। এবার প্রথমবারের মতো সে শব্দ শুনতে পায়। দূর থেকে কে যেন কাগজ ছিঁড়ছে-শব্দটা এমন।
পরিবেশ নিশ্চয়ই প্রচণ্ড প্রতাপে সবকিছুকে একেবারে বিশ্লিষ্ট করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তারচেও ক্ষমতাবান কেউ নিজের ক্ষমতা দিয়ে বোম্যানকে ঘিরে রেখেছে চতুর্পাশে।
অগ্নি চূড়া তার চারপাশে মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে উঠছে আর নামছে, এ দৃশ্য শুধু অপার্থিব, অদৃষ্টপূর্বই নয়, সত্যি সত্যি অকল্পনীয়। যেন পোডটা অন্য কোনো মাত্রায়, ভিন্ন কোনো জগতে বাস করে; তাকে ছোঁয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি সূর্যের শক্তিকে।
এবার সে দেখে যে এই নক্ষত্রের ভিতরটা আকৃতিহীন নয়। প্রকৃতিসৃষ্ট সব ধরনের গড়নই এখানে আছে।
প্রথমেই সে ছোট্ট ফোয়ারাগুলো দেখতে থাকে। এগুলো আকৃতিতে এশিয়া আর আফ্রিকার চেয়ে কোনো অংশে ছোট হবে না। সূর্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে, দাপড়ে বেড়াচ্ছে পিঁপড়ার মতো। অবাক ব্যাপার, নিচে কোনো সৌরকলঙ্ক চোখে পড়ল না। এটা হয়তো পৃথিবীর সূর্যের কোন ব্যক্তিগত রোগ।
এখানে সেখানে এক আধটু মেঘও দেখা যায়। ধোঁয়াও হতে পারে, কারণ সূর্যটা এত ঠাণ্ডা যে এর বুকে আগুনের শিখা তৈরি হওয়া সম্ভব। সাধারণ সূর্যে আগুনের শিখা বহু দূর-অস্ত বিষয়। সেখানে পদার্থ তার তিন অবস্থাকে পিছনে ফেলে প্লাজমা হয়ে থাকে। এখানে রাসায়নিক যৌগ তৈরি হয়ে আবার প্রাজমায় পরিণত হওয়ার আগে দু-চার সেকেন্ড সময় পেলেও পেতে পারে।
নক্ষত্রের উপরিতল জ্যোতির্ময় হয়ে যাচ্ছে। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় বোম্যানের। এখন সে কী করবে? চোখে তো সাদা বামন নক্ষত্র সহ্য করা সম্ভব নয়। ছোট নক্ষত্রটা উঠে আসার সময় চোখ বন্ধ করে রাখে।
সে চোখ মেলে বড় সূর্যের অন্য দিকে তাকিয়ে। আগুনের ঘূর্ণিঝড় উঠেছে নতুন অরুণোদয়ের সাথে সাথে। সে একবার ক্যারিবিয়ানের বুকে জল-ঝড় দেখেছিল। ঘূর্ণিপাকটা ছিল সচল। এই আগুনে ঘূর্ণিও হুবহু এক, শুধু এর গা আগুনের তৈরি আর আকৃতি পৃথিবীর সমান।
এরপর সে ঠিক নিচে এমন একটা কিছু দেখে যা আগে সেখানে থাকলে অবশ্যই চোখে পড়ত। নিচে গ্যাসের একটা বিরাট দল তৈরি হয়েছে এইমাত্র। তারা চারদিকের তাপ সহ্য করতে না পেরে দল বেঁধে উপরদিকে বাঁকা হয়ে সাঁতরে উঠছে-যেমন করে স্যামন মাছ ওঠে।
এমন আরো হাজারটা চোখে পড়ল একটু চেষ্টা করতেই। সেসব অঞ্চল আসলে ফিতার আকারে গ্যাস সাম্রাজ্য। সে ঠিকমতো দেখতে পায় না, তবে বোঝা যায় যে শত শত মাইল লম্বা হবে প্রত্যেকে।
তারা প্লাজমা মেঘও হতে পারে যা কোনো অজানা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফল। এই হল সবচে সহজ সরল ব্যাখ্যা। কিন্তু আচরণটা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না সে। সবাই দল বেঁধে সাদা মনের আগুন-স্তম্ভের উপর উঠে পড়ছে এবার।
একি কোনো জোরপূর্বক দখল, নাকি আলোর দিকে আলো কণার যাত্রা? যাই হোক, সে আন্তঃনাক্ষত্রিক অভিবাসন দেখতে পেল এইমাত্র। বড় সূর্য থেকে ছোটটার দিকে এই যে আগুনের সেতু বেয়ে অসীম পদার্থের গ্যাস হয়ে চলে যাওয়া তা আদৌ প্রাকৃতিক নাকি কোনো অদৃশ্য হাতের খেলা তা সে বুঝে উঠতে পারে না।
সে এক নতুন সৃষ্টির খেলা দেখছে, এ খেলার কথা ভাবার মতো, ফুরসৎ মিলবে না মানবজাতির। কিন্তু এর সবই সে বুঝতে পারবে এমন বোকামির আশা করাটাও বোকামি।
অধ্যায় ৪৪. অভ্যর্থনা
আগুনের সিঁড়ির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ডেভ বোম্যান বুঝতে পারে তার চারপাশে একটা কিছু ঘটছে। তরল পানির মতো আগুনে দুনিয়া যেন প্রবাহিত হচ্ছে। আলো কমে আসছে। দ্বিতীয় কোনো সূর্যাস্তের সময় চলে এসেছে। এরপর হঠাৎ করেই উপলব্ধি করে যে এখানে আলোর উৎস সূর্যটা নয়, বরং নিচের পৃথিবী।
মনে হচ্ছে ধোয়ার দেয়াল গজিয়ে উঠেছে তার চারপাশে, লাল জ্যোতিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে অচেনা পরিবেশে নেয়ার জন্য। আস্তে আস্তে ঘন হয়, সাথে সাথে সৌর ঝড়ের মৃদু গর্জনও হারিয়ে যায় আড়ালে। এখন পোডটা একেবারে কালিগোলা অন্ধকারে ঠায় ভেসে আছে; একটু পর সামান্য ঝাঁকিতে বোঝা গেল কোনো শক্ত সারফেসে এবার স্পেস পোডটা বসার সুযোগ পেয়েছে।
কিন্তু কিসের উপর? আলো ফিরে আসার সাথে সাথে চারপাশে যা দেখল তাতে তার নিজেকে পাগল ভাবতে আর বাকী নেই।
সে যে কোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল, প্রস্তুত ছিল না শুধু পরিচিত কিছু দেখার জন্য।
পোডটা এক চমৎকার পালিশ করা ঝকঝকে হোটেল স্যুটের মেঝেতে অবতরণ করেছে। এ অত্যন্ত দামী কামরা শুধু পৃথিবীর বিরাট বিরাট শহরের পাঁচ তারা হোটেলগুলোতেই দেখা যেতে পারে। এ হল স্যুটের থাকার ঘর। লিভিংরুমটায় একটা কফি টেবিল, ডিভান, এক ডজন চেয়ার, রাইটিং ডেস্ক, নানা ধরনের টেবিল ল্যাম্প, আধ ভর্তি বুককেস আর বেশ কিছু ম্যাগাজিন, এমনকি এক স্থানে সাজানো তাজা ফুলও চোখে পড়ে। ভ্যান গগের ব্রিজ এট আর্লস শোভা পাচ্ছে এক দেয়ালে, অন্যটায় ইয়েথের ক্রিস্টিনা’স ওয়ার্ল্ড। সে নিশ্চিত, ডেস্কের ড্রয়ার খুললেই একটা বাইবেল পাবে সেখানে…
ডেভ বোম্যান আসলেই পাগল হয়ে গিয়ে থাকলে তার ডিলুশনগুলো বেশ সুন্দরভাবেই সাজানো হয়েছে তো! সব ঠিকঠাক আছে, পেছনে ঘোরার পর কিছুই হারিয়ে যায়নি। আসলে সে যতটা চাপ সহ্য করেছে একজন মানুষের পক্ষে তার হাজার ভাগের এক ভাগও সহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং মানসিক বিকৃতি আসা তেমন অস্বাভাবিক নয়। পুরো দৃশ্যে বেমানান যে অংশ চোখে পড়ে তা হল তার স্পেস পোড।
জিনিসটাকে এত বাস্তব দেখাচ্ছে যে সেটাই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সম্ভবত তার মনকে যাচাই করা হচ্ছে দৃষ্টিবিভ্রমের সাহায্যে। নাকি সেই ক্ষমতাবানের দল তাকে স্বর্গ-নরক দেখিয়ে এবার মর্তে নামিয়ে দিয়েছে? বলছে, যাও, গিয়ে সবাইকে বলো আমাদের কথা। আমরা আছি, তোমাদের পাশে পাশেই সর্বশক্তি নিয়ে আছি…
ভাবনাটা তাকে কাঁপিয়ে দেয়। পোডের দরজা খোলার সাথে সাথে মৃদু শব্দ ওঠে চাপ সমতাকরণের জন্য।
সে পোডের বাইরে পা রাখে। স্থানটা একেবারে কঠিন…অবশ্যই, নাহলে স্পেসপোড থাকে কী করে?
কিন্তু বাতাসের ভয়তো কেটে যায়নি। সে নিশ্চিত ঘরটা হয় ভ্যাকুয়াম, নয়তো দূষিত বায়ুর বস্তা। কেউ এতকিছুর পরে এমন নিখুঁতভাবে খুতখুতে ভাব দেখাবে না, কিন্তু সে আলাদা বলেই এ পর্যন্ত টিকে আছে। তার আগে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা চাই। জীবন খোয়াতে আপত্তি ছিল না, আবার বিনা চেষ্টায় কখনো জীবন দিতেও রাজি নয়। তার ব্যক্তিত্ব এমন, তার উপর ট্রেনিং তাকে আরো বেশি বাস্তববাদী করে তুলেছে। দেখেশুনে যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও এমন হোটেল আছে বলে মনে হচ্ছে।
হাত উপরে তুলে ছেড়ে দিতেই সেটা ধপাস করে নেমে এল। তার মানে মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মতো। সব কেমন গোলমেলে লাগছে। হিসাব করে প্রতিটি সেকেন্ড চলতে হবে।
সে দেয়ালের পাশে যায়, ছুঁয়ে দেখে, যায় কফি টেবিলের পাশে। এর মধ্যে বেয়ারা ডাকার বেলও আছে। একটা ভিশন ফোন আর তার পাশে স্থানীয় ফোন ডাইরেক্টরিও পড়ে আছে। সে স্পেসস্যুট পরা হাতে তুলে নেয় বইটাকে।
জীবনে হাজারবার এমন নামের টেলিফোন বই হাতে নিয়েছে বোম্যান। ওয়াশিংটন ডি.সি.।
এবার সে ভালমতো লক্ষ্য করে বুঝতে পারে যে এ সব সত্যি হতে পারে, কিন্তু সে সম্ভবত পৃথিবীতে নেই।
এলাকার নামটার পর বাকী লেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। সেগুলো দারুণ ঝাপসা। ব্যাপার বোঝার জন্য পাতা উল্টে নিয়ে দেখতে পেল সব ফাঁকা, কোনো লেখা নেই। এমনকি কাগজের জিনিসটাও ঠিক কাগজ নয়, কেমন যেন কোঁচকানো সাদা জিনিসে গড়া। দেখতে অবশ্য খুব বেশি এদিক-সেদিক নয়।
সে টেলিফোন তুলে নিয়ে ডায়াল করে; যা ভেবেছিল তাই। কোনো শব্দ নেই।
সুতরাং, এ এক নিখুঁত ভাওতাবাজী। কিন্তু এই ভাওতাবাজী নিশ্চয়ই তাকে একটু শান্ত করার জন্যে, সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। যাই হোক, সে আর স্পেসস্যুট খুলছে না।
চেয়ারগুলো দুনিয়ার ওজন নিয়ে বসে আছে, টেবিলের কোনো ড্রয়ার খুলছে না। বইগুলো দেখেও হতাশ হতে হল। গত তিন বছরের সেরা সেরা হাজার রকমের বই এখানে। বুকসেলফ থেকে তোলারও উপায় নেই।
দুটো দরজা বেশ সাবলীলভাবে খুলে গেল। প্রথমটা দিয়ে বেডরুমে যাওয়া যায়, সেখানকার লাইটগুলো জ্বালানো-নিভানো যাচ্ছে। অন্য দরজা খুলে ভিতরে দেখতে পায় একটা ক্লোজেট। ক্লোজেটে চারটা স্যুট, ডজনখানেক শার্ট, কয়েকটা আন্ডারওয়্যার আরামে ঝুলছে।
একটা স্যুট নামিয়ে এনে চোখের সামনে ধরে সে বুঝতে পারে যে জিনিসটা ফারের নয় বরং উলের মতো কিছু দিয়ে তৈরি। পোশাকটা একটু পুরনোও বলতে হবে, পৃথিবীতে গত চার বছর ধরে কোনো মানুষ সিঙ্গেল ব্রেস্টেড কোট পরে না।
বেডরুমের পর একটা বাথরুম ছিল। সে হাজারো স্বস্তির সাথে অনুভব করে যে তার বাথরুমটা ডামি নয়, কাজ করছে ভালমতো। এর পাশেই একটা পিচ্চি রান্নাঘর। সেখানে ইলেক্ট্রিক কুকার, ফ্রিজ-এসবই আছে। সে এসব দেখা শুরু করেছে শুধু আগ্রহের কারণে নয়, পর্বতপ্রমাণ খিদের জ্বালায়ও।
ফ্রিজের ভেতর পরিচিত অনেক ধরনের ক্যান আর প্যাকেট, ঠাণ্ডার ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে একটু কুয়াশা কুয়াশা ভাব দেখে। প্যাকেটগুলোর লেখা কাছ থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু বোঝানো হচ্ছে যে লেখাটা ইংরেজি।
একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে সে হতাশ হয়-সেখানে ডিম, দুধ, মাছ মাংস বা সজির মতো কোনো রান্নার যোগ্য খাবার নেই। সব প্যাক করা খাবার।
সে কিছু পরিচিত নাস্তার প্যাকেট তুলে নেয়। ভেবে একটু মজা পায়, এসব ফ্রিজে রাখার কথা না। প্যাকেট তোলার সাথে সাথেই বুঝতে পারে সেখানে কর্নফ্লেক্স নেই। জিনিসটা অনেক বেশি ভারি।
প্যাকেট খুলে সে হালকা নীলচে আঠালো এক ধরনের খাবার দেখতে পায়। ওজনে পুডিংয়ের মতো। রঙ-গন্ধের তোয়াক্কা না করে ক্ষুধার কাছে নত হতে হচ্ছে।
হঠাৎ করেই নিজের চুল টেনে তুলে ফেলতে ইচ্ছা করে তার। ব্যাপারটা হাস্যকর হলো না? আমি যদি কোনো বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় পড়ে থাকি তো এর মধ্যেই ফেল মেরে বসেছি। এখনো স্পেসস্যুট না খোলা উচিত হয়নি।
সে সাথে সাথে বেডরুমে ফিরে গিয়ে নিজের হেলমেট খোলার কাজে মনোযোগ দেয়। একটু আলগা করেই বাতাস নিয়ে বুঝতে পারে চারপাশে তার বিশুদ্ধ বাতাসের ছড়াছড়ি।
সাথে সাথে হেলমেটটা বিছানায় রেখে ভালমতো স্যুট খুলে ফেলে। তারপর ভদ্রভাবে কয়েকবার বাতাস টেনে নিয়ে ক্লোজেটের অন্য পোশাকের সাথে ঝুলিয়ে দেয়। দেখতে একটু বেখাপ্পা লাগলেও করার কিছু নেই। মানবজাতিকে সুন্দররূপে উপস্থাপন করতে হবে তো! তার উপর তার আছে একজন জ্যোতির্বিদের নিয়মানুবর্তিতা।
বোম্যান রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে পরের প্যাকেটগুলো দেখার কাজে মনোযোগ দিল। সেগুলোতেও একই জিনিস। অগত্যা নীলচে আঠালো তরলের গন্ধ নিয়ে খুব একটা খারাপ লাগল না। জিনিসটায় ম্যাকারনির মতো মসলা মসলা ঘ্রাণ আছে। সে সাবধানে পুডিং থেকে একটু ভেঙে হাতে নেয়, তারপর ভাবে, তাকে বিষ দেয়ার কোনো ইচ্ছা নিশ্চয়ই তাদের নেই; কিন্তু বায়োকেমিস্ট্রির মতো একটা ঘোরালো বিষয়ের জন্য একটু ভয় ভয় হচ্ছে।
মুখে দিয়ে প্রথমে সে একটু চুষে দেখেই চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। এর স্বাদ-গন্ধ আমেজ অনন্য। চোখ বন্ধ করে খেলে জিনিসটাকে মাংসও মনে হতে পারে, নরম রুটিও মনে হতে পারে আবার শুকনো ফলও মনে হতে পারে।
এবার একটা ক্যান খুলে সেখানে বিয়ার না পেয়ে সে খানিক হতাশ হয়। একই জিনিস। সুতরাং খাবারগুলো একটু বিরক্তিকর ঠেকবে এক সময়। পানি ছাড়া তরল কিছু নেই।
সে প্রথমে দু-এক ফোঁটা পানি চেখে দেখে, স্বাদটা অপূর্ব। তারপর নিজের সন্দিহান মনের জন্য একটু লজ্জা পেয়েই যেন বাকীটা এক চুমুকে শেষ করে ফেলে।
পানিটা তবু কেমন কেমন মনে হয়। এ হল একেবারে খাঁটি পানি এবং শুধু এইচ টু ও। আর কিছু নেই এই পানির মধ্যে। আতিথেয়তাকারী তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এক বিন্দু ঝুঁকি নিতে চায় না মনে হচ্ছে।
গোসলের সময় সাবান না পেয়ে মন যতটা খারাপ হয়েছিল তা পুষিয়ে গেল এয়ার ড্রায়ারে শরীর শুকিয়ে। এবার ক্লোজেট থেকে কাপড় নিয়ে পরার পালা।
শুয়ে শুয়ে দেখার জন্য যথারীতি রুমের সিলিংয়েও একটা হোটেল টাইপ সিলিং টিভি আছে, সেটাও খেলনা হবে তাতে আর সন্দেহ কী?
কিন্তু তার বিছানার পাশে কন্ট্রোল ডিস্কটা দেখে এত বাস্তব মনে হল যে সাথে সাথে সেটার অন বাটন চেপে দেয় বোম্যান।
সাথে সাথে চিত্র ভেসে ওঠে মনিটরে। এ লোক খুবই পরিচিত একজন আফ্রিকান ধারাভাষ্যকার, লোকটা সেই পরিচিত সুরে নিজের দেশের বন্যপ্রাণী বাঁচানোর আন্দোলনের কথা বলছে। সে জানতো না মানুষের কণ্ঠস্বর এত মধুর, এত প্রয়োজনীয়, এত দামী। মুহূর্তে জীবন ফিরে আসে তার মনোজগতে।
এর পর অন্য চ্যানেলে ওয়াল্টনের ভায়োলিন কনসার্তো বা বেহালা কনসার্ট দেখতে পায়। দেখতে পায় আরো কত অনুষ্ঠান কত শত চ্যানেলে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। অনুষ্ঠানগুলো মনকে শুধু সজীব করে তোলেনি, সাথে সাথে তার একটা সন্দেহও প্রকট হয়ে উঠেছে।
এই সবকিছুই মানুষের টি এম এ-ওয়ান আবিষ্কারের পর পর রেকর্ড করা হয়। তার মানে মানুষ যেটুকু ধারণা করেছিল টি এম এ-ওয়ান তারচে অনেক বেশি কাজ করে। সব কিছু সম্প্রচার করেছে অহর্নিশি।
এরপর একটা নাটকে সে তার নিজের লিভিংরুমে বসে থাকা অতি বিখ্যাত এক চিত্রতারকার দৃশ্য দেখে বিমূঢ় হয়ে যায়। সে বেডরুমে ঢুকছে, এমন সময় বোম্যানও সেই দরজার দিকে তাকায়।
কিন্তু কেউ প্রবেশ করে না। ওদিকে ছবিতে সেই লোক এরিমধ্যে বিছানায় উঠে বসেছে।
তার মানে এই পরিবেশ সেই ছায়াচিত্রের নকল। এজন্যেই টেলিফোন বুকের বড় লেখা পড়া গেলেও ছোটগুলো পড়া যায়নি।
নিজের আঙুলগুলো মাথার পেছনে চালিয়ে দিয়ে টিভি বন্ধ করে স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থেকে এবার সে ভাবে-কী করব এখন?
শারীরিক আর মানসিক-দু-দিকদিয়েই একেবারে ক্লান্ত ডেভ বোম্যান। কিন্তু এ পরিবেশে ঘুমানোর কথা চিন্তাও করা যায় না।
কিন্তু শরীর, মন আর আরামদায়ক বিছানা তার বিপক্ষে চলে যাচ্ছে।
ক্লান্তি টের পেয়ে কোনোমতে লাইট নিভিয়েই সে অসাড় হয়ে যায়। এবার সে স্বপ্ন রাজ্যের চেয়েও দূরে কোথাও চলে গেছে।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাশচারী জ্যোতির্বিদ ডেভিড বোম্যান শেষবারের মতো ঢলে পড়েছে ঘুমের কোলে।
অধ্যায় ৪৫. পরিণতি
আর কোনো প্রয়োজন না থাকায় পুরো হোটেল স্যুটটাই এর স্রষ্টার মনে বিলীন হয়ে গেল। শুধু আছে সেই খাট, খাটের বাইরে প্রতিরক্ষা শিল্ড আর খাটের উপর স্বপ্নহীন অপূর্ণ নিদ্রারত আধা-সচেতন ডেভ বোম্যান। বাইরে আগুনের হল্কা, ভিতরে নিরুদ্বিগ্ন ডেভিড, আশপাশে অবোধ্য অনুভূতি। নেই ভয়, শঙ্কা, আশা, হতাশা; কিছুই নেই।
সে যেন কোন্ অজানার দেশে ভেসে আছে, চারপাশে আদিগন্ত কালো সুতোর রেখা নানা ক্ষেত্র গড়ছে, ভাসছে অজস্র ছোট ছোট আলো-কোনটা স্থির, কোনোটা অকল্পনীয় গতিতে চলমান।
সে একবার মানুষের ব্রেনের এক ছোট্ট টুকরোকে মাইক্রোস্কোপের নিচে ধরেছিল। সেই হাজারো সুতোর গোলকধাঁধা ছিল মৃত, কিন্তু চারপাশের অজস্র বিস্তৃতির পুরোটাই যেন জীবন্ত।
সে জানে, অথবা মনে করার চেষ্টা করে যে জানে এই রহস্যের সমাধান। সে এক দুনিয়াজোড়া মাথার কাজের ধারার ভিতরে বসে আছে। জীবন্ত মস্তিষ্ক। সেখানে অকল্পনীয় বিস্তৃত সব কাজ চলছে অবিরত, কিন্তু দেখা যায় না। শুধু অনুভব করা যায় নিজের অপরিমেয় ক্ষুদ্রতা।
এই দৃশ্য, অথবা দৃষ্টিভ্রম চলে যায় এক মুহূর্ত পরেই। সেই স্ফটিকীকৃত জগৎ, সেই আলোর গোলকধাঁধা, সেই অকল্পনীয় অবস্থা কাটার পর পরই সে একটা সচেতনতার ভুবনে ভাসতে শুরু করে।
প্রথমে মনে হল স্বয়ং সময় পেছনে চলে যাচ্ছে। সে ব্যাপারটাকে মেনেও নেয় আসল সত্যি জানার আগ পর্যন্ত।
পুরনো অনুভূতি, দৃশ্য, মনোভাব, স্বাদ, তৃপ্তি-সব ফিরে আসছে, চলে যাচ্ছে। হোটেল রুম-জ্বলন্ত লাল নক্ষত্র- স্টেশন- প্রবেশদ্বার- জ্যাপেটাস- ডিসকভারি শনি- বৃহস্পতি- চাঁদ- পৃথিবী- ট্রেনিং… সব, সব ফিরে আসছে। ক্রমবর্ধমান গতিতে যেন তার স্মৃতির ফিতা পেছনে টানে কেউ একজন। কিছুই হারায়নি, কিন্তু মানুষের মন কি এত নিখুঁতভাবে সব সংরক্ষণ করে রাখে?
এগিয়ে আসছে সহজ-সরল পৃথিবী, আনন্দময় অতীত, বেদনায় নীল হয়ে যাওয়া সব মুহূর্ত। প্রিয়মুখ, প্রিয় কাজ, কৈশোর, শিশুত্বও এক সময় কেটে গেল।
এখন স্মৃতির মহা সুড়ঙ্গ শুকিয়ে আসছে। সময় বইছে অতি, অতি ধীরে। পরের চক্র শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত পেন্ডুলামের মতো দুলছে মহাকাল; এদিক-ওদিক।
সময়হীন মুহূর্ত কেটে গেল, পেন্ডুলামের দোলনের দিক গেল বদলে। থেমে গেল সবকিছু। সব, সবকিছুর উল্টোরথ শুরু হয়েছে আবার।
এক দ্বৈত নাক্ষত্রিক এলাকায়, পৃথিবী থেকে বিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে এক শিশু তার চোখ খুলে প্রথমবারের মতো কেঁদে ওঠা শুরু করবে এখন।
অধ্যায় ৪৬. এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর
এক সময় সে নিরব হয়ে যায়, কারণ এখন আর সে একা নয়।
এক ভৌতিক ঝকঝকে চতুষ্কোণ আকাশে উদিত হয়েছে। সেটা এক ক্রিস্টাল ট্যাবলেটে পরিণত হয়ে এক সময় স্বচ্ছতা হারায়। এর ভিতর দুধসাদা আবহ।
অস্পৃশ্য, ভৌতিক কিছু শরীর ঘোরাফেরা করে তার উপরিতলে, ভেতরে। তারা জোড়ায় জোড়ায় একত্র হয়, তারপর কাঠির মতো সরু হয়ে যায় প্রত্যেকে, তারপর ঘুরতে থাকে; আলোর বৃত্ত তৈরি করে। যেন পুরো মহাকাশ জুড়ে রয়েছে তার ব্যাপ্তি।
এ আলোকসামান্য দৃশ্য যে কোনো শিশুর, যে কোনো বন মানুষের মনোযোগ আটকে রাখতে জানে। কিন্তু এ দৃশ্য ত্রিশ লাখ বছর ধরে সত্যিকার কাজের কাজ কিছুই করেনি। সে শুধুই মনোযোগ আটকে রাখে। বাকী আসল কাজটা হয় মনের গহীনে।
এবার কাজের ধারা অতি দ্রুত এগিয়ে চলে, কারণ নতুন পদ্ধতি বেরিয়েছে।
শিশু তার চোখ তুলে ক্রিস্টালের গভীরে তাকায়। এ চোখ মানুষের চোখ নয়। সে দেখতে পায় ঘুমিয়ে থাকা রহস্যলোকের দরজাকে, কিন্তু এখনো ঠিক বুঝতে পারে না। সে জানে এখন সে সবচে নিরাপদ অবস্থায় আছে, কারণ এখানে লাখো প্রাণীর জন্ম হয়েছে। কিন্তু সে এখনো জানে না সামনে সবচে অদ্ভুত জন্মটা এখনো বাকী।
এবার, স্বচ্ছ মনোলিথ তার আলোর খেলা বন্ধ করে দেয়; হারিয়ে যায় নিজের আলোরই মতো; তারপর শূন্য থেকে উঠে আসা প্রতিরক্ষা বর্ম মিলিয়ে যায় শূন্যে; এবং, এক বিশাল দানব লাল নক্ষত্র তার এলাকার অহেতুক বর্মটা মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে সেটুকু দখল করে নেয়।
সেই স্পেস পোডের ধাতু আর প্লাস্টিক, এক সময় যে লোকটা নিজেকে ডেভিড বোম্যান বলে পরিচয় দিত তার সমস্ত পোশাক আর তার সাথে যা ছিল সব সাথে সাথে প্লাজমার অকল্পনীয় উত্তাপে লীন হয়ে যায় সূর্যের সাথে।
আরামদায়ক উষ্ণতাতেও সেই শিশু ভয় পেয়ে বুঝতে পারে যে সেসব পদার্থের তার প্রয়োজন আছে। নাহলে কিসের দিকে সে তার ক্ষমতা আর দৃষ্টিশক্তিকে তাক করবে? তার ধ্বংসাতীত শরীরটা তার নিজের মনের বর্তমান প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছু নয়। এবং এতসব থাকা সত্ত্বেও, সে জানে, সে এক শিশু, মাত্র একটা শিশু।
তাই এখনো বুঝে উঠতে পারছে না যে তার আর পদার্থের প্রয়োজন নেই, নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের সবচে ভাল ক্ষেত্র হচ্ছে শক্তি।
এবং সময় এসেছে যাবার। অবশ্য এক অর্থে সে কখনোই জন্মস্থান ছেড়ে যাবে না, কারণ জন্মের সময় তার অস্তিত্বের একটা অংশ মিশে গেছে দ্বৈত নক্ষত্রের চির দ্বৈরথের সাথে। কোন্ এক অজানা, অকল্পনীয় উদ্দেশ্য যেন মিশে আছে সেখানে। তার লক্ষ্য এখন সে জানে। কিন্তু যাবার জন্য সেই প্রাচীন পথ ধরতে হবে না। সে ত্রিশ লাখ বছরেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, সৃষ্টি জগতের পেছন দিয়ে যাওয়া ছাড়াও যাতায়াতের আরো সহজ সহজ রাস্তা ছড়িয়ে আছে চারপাশে। নক্ষত্র দুয়ারের মান্ধাতা প্রযুক্তি তার যথেষ্ট সেবা করেছে, কিন্তু আর কখনো সেসবের প্রয়োজন নাও পড়তে পারে।
সেই আভাময় চতুষ্কোণ, যেটাকে প্রথমে সামান্য এক স্ফটিক মনে হয়েছিল তা এখনো তার সামনে ভাসছে। এর ভিতরে সময় আর স্থানের কত অযুত নিযুত রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু এখন সে অন্তত একটা ব্যাপারে কর্তৃত্ব খাটাতে পারে। কী অপরিহার্য, কী প্রয়োজনীয় এই ১:৪:৯ অনুপাত! কী দুঃখজনক ব্যাপার, এই সিরিজ মাত্র তিন মাত্রাতেই ফুরিয়ে গেছে।
সে তার মনকে এই জ্যামিতিক সারল্যের দিকে তাক করানোর সাথে সাথে এর ভিতর মহাকাশ-রাজ্যের কালিগোলা অন্ধকার প্রবেশ করে। নিভে যায় লালচে আগুন-সমুদ্র, প্রবেশ করে কোথায় যেন…এবং অবশেষে, তার সামনে সেই চির নিশীথের রঙের উপর ফুটে ওঠে এক জ্যোতির্ময় ঘূর্ণিপাক। মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি।
মনে হতে পারে প্লাস্টিকের উপর একটা মডেল, কিন্তু এই হল পুরো গ্যালাক্সির রূপ, রস, গন্ধ। এবং এই শিশুর তালুবন্দী। সে চাইলেই এই পুরোটার দশ সহস্র কোটি নক্ষত্রের যে কোনোটায় মনোনিবেশ করতে পারে। সে চাইলে এরচে বেশি কিছু করতে পারে।
এখন সে এই সৌর-নদীতে ভেসে যাচ্ছে। এখন সে গ্যালাক্টিক কোরের মাঝপথে। সেখানে ঝলমল করে অযুত নক্ষত্র, আর পেছনে, প্রান্তসীমায় একা একা পাহারা দেয় কিছু নিঃসঙ্গ তারার দল।
সে জানে, সামনের এই আকৃতিহীন এলাকায় এখনো জোয়ার আসেনি, এখনো বিবর্তনের প্রাথমিক উপাদান গড়ে ওঠেনি, এখানে সময় বলতে কিছু নেই। এই শূন্যতায় আলো নেই, আলোর সৃষ্টি উপাদানও নেই। এখানে আলো জ্বলবে, কায়া তৈরি হবে, সময় তৈরি হবে, তারপর জীবনের অপার স্রোত ভাসিয়ে দেবে দশ দিগন্ত, ঝলমলিয়ে উঠবে চারদিক। বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পরে।
সে খেয়াল না করে এমন একটা এলাকা পেরিয়েছিল, এবার সচেতনভাবেই সেখানে প্রবেশ করে। শিউরে ওঠে একাকিত্বের প্রকৃতি দেখে।
এই গ্যালাক্টিক মহাসাগর তাকে শীতল করে দেবে সেই ভয় নেই। সৃষ্টিহীনতার বিষাদ তার মর্মে মর্মে ধ্বনিত হচ্ছে। এবার সে বুঝতে পারে কেন ত্রিশ লাখ বছর ধরে ওরা শুধু ফুল ফোঁটানোর সাধনারত। কিন্তু তার একাকিত্ব তবু একটুও ঘোচে না।
এরপর হঠাৎ করেই বুঝতে পারে যে সে কখনোই একা হবে না। সাথে সাথে সৃষ্টি জগতের স্ফটিক-স্বচ্ছ রূপ তার মুঠোয় ধরা দেয়; পুরোপুরি তার নিজের ইচ্ছায় নয়, সে বুঝতে পারে।
সে আবার অযুত, নিযুত আলোকবর্ষ উপরে উঠে যায়, যেখানে পুরো মিল্কি ওয়ে একটা বিন্দু, তারপর নামতে শুরু করে। চারপাশে ছিটকে বেরোয় তারকারাজি, নেবুলা, গ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ। নক্ষত্রগুলোর ভিতর দিয়ে, সব বস্তুকে ভেদ করে সে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোয়। কসমিক ধুলোবালির দিকে প্রায় চোখই পড়ে না।
নক্ষত্রগুলো ছোট হয়ে হয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল। কালো আকাশে হারিয়ে যাচ্ছিল মিল্কি ওয়ে।
এবং অবশেষে সে হাজির হয়েছিল সেখানে, যেখানে তার যাবার ইচ্ছা, যেখানে সে আগে ছিল, যেখানটাকে মানুষ বলে-বাস্তব।
অধ্যায় ৪৭. শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে, লুকানো রবে না মধু চিরদিন তরে …
এখানে, ওর ঠিক সামনে এক বিশাল খেলনা ভেসে বেড়াচ্ছে, কোনো নক্ষত্র জাতক একে প্রতিহত করতে পারবে না। পৃথিবী নামক গ্রহটি তার স-ব মানুষ নিয়ে ভেসে চলেছে কোন্ অজানার উদ্দেশে!
সে ফিরেছে সময়মতো। হয়তো অনেক নিচে, জনবহুল নগরীগুলোয় রাডার স্ক্রিন জুড়ে দাপড়ে বেড়াচ্ছে অ্যালার্মের লাল আলো। আকাশ ছত্রখান করে ফেলছে দানবীয় টেলিস্কোপগুলো। এবং মানুষ যে ইতিহাস জানে হয়তো তার যবনিকাপাত হবে এ যাত্রায়।
হাজার মাইল নিচে একটা মৃত্যু-দৃত জেগে উঠেছে…সে বুঝতে পারে। সেই কার্গোটা উঠে আসছে নিজের অর্বিটে। তার কাছে এর ভিতরের অস্থির অসীম শক্তির কোনো মানেই নেই, কিন্তু সে আরো পরিষ্কার এক আকাশ আশা করেছিল। নিজের ইচ্ছাটাকে সামনে বাড়ায়, ঘুরন্ত মেগাটনের জিনিসটা এক নীরব বিস্ফোরণে কৃত্রিম সূর্যোদয় নিয়ে আসে ঘুমন্ত অর্ধ ধরিত্রী জুড়ে। আণবিক মেঘ ঝরে পড়ে কুমারী বনভূমির সবুজ-সুন্দরের বুকে।
এরপর সে প্রতীক্ষা করে, নিজের সবটুকু চিন্তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। বোঝার চেষ্টা করে নিজের আজো অচেনা শক্তিকে।
আজ সে জগদীশ্বর হলেও ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কী করতে হবে এরপর।
কিন্তু সে হয়তো কিছু না করার কথা ভেবে রেখেছে।
***
আর্থার সি ক্লার্ক
সাহিত্যচর্চার একটা পরিবেশের জন্য অনেকেই অনেক কিছু করেছেন। এক্ষেত্রে কতটা নিবেদিতপ্রাণ হলে একজন মানুষ অধুনা সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ব্রিটেন ছেড়ে টগবগে যৌবন থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত থাকেন শ্রীলংকার মতো দ্বীপদেশে-অর্ধশতাব্দীরও বেশি কাল ধরে, আসলেই তা বিবেচ্য বিষয় সেই লেখক, তাঁর লেখা, লেখনীর বৈশিষ্ট্য-সর্বোপরি লেখকের জীবন আর মানব জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আলোকপাত করার ক্ষেত্রে। তিনি ক্লার্ক, আর্থার চার্লস ক্লার্ক। বড় মাপের একজন লেখকই নন, লেখকের মাপকাঠি হিসেবেও বিবেচিত। তিনিই সর্বকালের সফলতম এস এফ ছায়াছবির চিত্রনাট্যকার, আজ পর্যন্ত একটা সায়েন্স ফিকশন লিখে তাঁরচে বেশি টাকা কেউ পায়নি। সোজা কথায় জীবিতদের মধ্যে তিনিই এস এফ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আর সর্বকালের হিসেবে দ্বিতীয়।
‘আর্থারকে, যিনি চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন আমি পা রাখার আগেই’ কথাটা লিখেছিলেন অলড্রিন। চন্দ্রবিজয়ী। আর্থার সি ক্লার্কের ড্রয়িংরুমের দেয়ালে ঝোলানো ছিল একটা টি শার্ট। ওতে লেখা এই অসাধারণ উক্তিটি- যা দেয় ক্লার্কের কাজ আর জীবনের স্বীকৃতি।
আর্থার সি ক্লার্ক অ্যাপোলো এগারো, বারো ও পনের মিশনের ধারাভাষ্যকার ছিলেন। পৃথিবীবাসীর কানে তাঁর কণ্ঠ থেকে ভেসে আসা বিবরণেই পৌঁছে গেছে। চাঁদে গমনকারী অভিযাত্রীদের অভিযানের কথা- ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের চিত্র। বাস্তব জীবনে সম্পৃক্ততা ছিল বিজ্ঞানের সাথে। সায়েন্স ফিকশন জগতে শক্তিময় লেখনীর জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন আর্থার সি ক্লার্ক। প্রথম যেদিন ভূ-স্থির কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে লেখেন, সেদিনও হয়তো তাঁর মতো অতি কল্পনাবিলাসী বিজ্ঞানবিদ ভাবেননি যে, জীবিতাবস্থায় তাঁরই লেখা তুলে আনবে বাস্তব সোনার ফসল। ভাবেননি, কোটি কোটি মানুষ তাঁরই কল্পনার বদৌলতে শত শত স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলে তথ্য প্রবাহের স্রোতে-বিনোদনের জগতে গা ভাসাবে। তিনি কি জানতেন যে, পৃথিবীর আবহাওয়া বিজ্ঞান, সমরনীতি, গোয়েন্দাগিরি, তথ্য প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অকল্পনীয় হারে ব্যবহৃত হবে তাঁরই মাথা থেকে আসা আইডিয়া? লেখাটি প্রকাশিত হয় হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের এক সপ্তাহ আগে। ‘ওয়ার্লেস ওয়ার্ল্ড’ নামক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায়।
স্যাটেলাইট বিজ্ঞানের জনক তিনি।
সচেতন জীবনের শুরু থেকে বিজ্ঞান তাঁকে নাড়া দিয়েছিল বেশ জোরেসোরেই। ছেলেবেলায় বাসায় বানানো টেলিস্কোপে চাঁদ ছত্রখান করার চেষ্টা করতেন। মামুলি দৃষ্টি দিয়েই। উনিশশো ছত্রিশে লন্ডন এসে ব্রিটিশ ইন্টার প্ল্যানেটারি সোসাইটিতে যোগ দেন। ব্রিটেনের রয়্যাল এয়ার ফোর্সে রাডার ইস্ট্রাক্টর ছিলেন একচল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ পর্যন্ত। এর পর লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে পদার্থ আর অঙ্কে ফার্স্টক্লাস সহ গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেন। তিনি ‘দ্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, ‘অ্যাকাডেমি অব অস্ট্রোনটিক্স’ সহ আরো বহু প্রতিষ্ঠানের অনারারি মেম্বার।
‘যা একবার পৃথিবীতে ঘটতে পারে তা লক্ষ লক্ষবার মহাবিশ্বে ঘটেছে বলে আশা করা যায়।’- এ কালান্তরী বিশ্বাসই তাঁকে দাঁড় করিয়েছে সায়েন্স ফিকশনের সামনে। তাঁর লেখার বয়সই অর্ধশতাব্দী পেরিয়েছে। শতাধিক বই লিখেছেন। গল্পের শব্দ গাঁথুনীতে বিজ্ঞানমনস্কতা ফুটিয়ে তুলতে পারদর্শী। বার্ধক্যের বানে জর্জরিত তিনি নিরন্তর বিজ্ঞান সাধনা করে যাচ্ছেন আজও। শ্রীলংকার যে জায়গাটায় ক্লার্ক থাকেন, ওখানকার নাম হয়েছে তাঁর নামে। একজন ক্যাব বা বেবিট্যাক্সি ওয়ালাকে ‘ক্লার্ক পয়েন্টে যেতে বলতে হয় না। ক্লার্ক শব্দটা উচ্চারণ করলেই হয়। এই আজো এ মানুষটা সারাটা দিন কাটান স্টাডি রুমে। তাঁর সার্বক্ষণিক সহকারী একজন শ্রীলংকান সায়েন্স ফিকশন রাইটার। তিনি মনে করেন ক্লার্কের কাছাকাছি আসতে পারাটাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওনা। শ্রীলংকার মানুষের চোখে তিনি “দ্য অনারারি রেসিডেন্ট”।
উনিশশো সতেরতে ইংল্যান্ডের মাইনহেডে জন্মগ্রহণ করেন ক্লার্ক। উনিশশো ছিচল্লিশ সালে, বেশ খানিকটা দেরিতেই লেখালেখির দরজায় পা রাখেন ‘রেসকিউ পার্টির মাধ্যমে। “প্রিয়ডিক্যাল অ্যাসফাউন্ডিং সায়েন্স’ পত্রিকাতে। তাঁর সাড়া জাগানো টেকনিক্যাল ব্যাপার ভিত্তিক উপন্যাস হচ্ছে ‘চাইল্ডহুডস এন্ড’ (১৯৫৩), ‘দ্য সিটি অব দ্য স্টার্স’ (১৯৫৬), এঁদেভু উইথ রামা’ (১৯৭৩), আর দ্য ফাউন্টেইনস অব প্যারাডাইস’ (১৯৭৯)। বিখ্যাত গ্রেট বেরিয়ার রীফ আর সিংহলের সাগরে ডুব দিয়ে কেটেছে সারাটা যৌবন। বৈজ্ঞানিক কাহিনী ভিত্তিক ছায়াছবিও করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক কল্পকথাভিত্তিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।
‘থ্রি থাউজ্যান্ড ওয়ান: দ্য ফাইনাল ওডিসি’র জন্য তিনি সাত অঙ্কের ডলার পেয়েছেন বলে মনে করা হয়। সংখ্যাটা না কি দু-এক মিলিয়ন নয়। এর মানে হল, টাকার হিসাব আঠার কোটির উপর। আর এটা শুধু ইংরেজির জন্য। আরো পঁয়ত্রিশ ভাষার কথা হিসাবে না নিলেও চলবে। তাঁর অর্ধশত বই শুধু ইংরেজিতেই দু কোটির উপর কপিতে বেরিয়েছে।
ক্লার্কের প্রভাব আর আওতা অনেক দূরে গিয়ে ঠেকে। খ্রিস্টিয় পোপ জন পল তাঁকে পোপের দেশ ভ্যাটিকান সিটিতে ডেকেছেন মহাকাশ যুগে মানুষ কেমন হতে পারে, ধর্মের সম্ভাব্য অবস্থা ও অবস্থান এবং মানুষের মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনার জন্য। এ লোকটা মনেপ্রাণে একজন সায়েন্স ফিকশন রাইটার। দীর্ঘ জীবনে তিনি সায়েন্স ফিকশন ছাড়া মাত্র দুটি উপন্যাস লিখেছেন। একটা ছেলেবেলা নিয়ে আর অন্যটা নিজের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রাডার অফিসারের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। ওটার নাম ‘গ্লাইড পাথ’। আর যেগুলো এস এফ নয় সেগুলো প্রবন্ধ।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন অন্যান্য দেশের মতো তারটিও ব্যস্ত ধ্বংসলীলায়- তখনো বিশ্বের সুবিধা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে তিনি স্যাটেলাইট সম্পর্কে লিখেছেন। ‘মার্কনি ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশীপ’ পান ওটার জন্য।
পেয়েছেন ফ্র্যাঙ্কলিন ইনস্টিটিউট স্বর্ণপদক, উনিশশো পঁচাশি সালে SCIENCE FICTION WRITERS OF AMERICA তাকে গ্র্যান্ড মাস্টার (Grand Master of Science Fiction) খেতাবে ভূষিত করে। উনিশশো ঊননব্বইতে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। বাষট্টি সালে কলিঙ্গ (ব্লদেভু উইথ রামা), উনসত্তর সালে আরেকটি পুরস্কার, র্যাডফোর্ড ওয়ারশার খেতাব, দু-বার হুগো, নেবুলা অ্যাওয়ার্ড, J.w. CAMPBELL খেতাব সহ আরো অনেক পুরস্কার জুটেছে তাঁর এ জীবনে। তবে কথাও থেকে যায়। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, পুরস্কারদাতারা তাঁকে পুরস্কৃত করে নিজেরাই বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছেন।
যে দু-বার নেবুলা পেয়েছেন:
১৯৭৩ Rendezvous with Rama
১৯৭৯ The Fountains of Paradise
আর হুগো এ্যাওয়ার্ড:
১৯৭৪ Rendezvous with Rama
১৯৮০ The Fountains of Paradise
ক্লার্ক ভবিষ্যতের বেসাতি করেন। তাই বিজ্ঞান কল্প গল্পকারদের জন্যও তাঁর একটা কথা আছে জানানোর মতো। তিনি সায়েন্স ফিকশন লেখার পেছনে সবচে বড় যে উদ্দেশ্যটা খুঁজে পেয়েছেন তা তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, “এসবের (ধর্ম- দর্শন সংস্কার-সমাজ-মূল্যবোধ) মধ্য দিয়ে নূতনতর জীবনবোধ কেমন দাঁড়াতে পারে, তা অনুসন্ধানের দায়িত্ব সায়েন্স ফিকশন রাইটারের। শুধু বিজ্ঞানকে জাদু হিসেবে উপস্থাপিত করার জন্যে নয়- এ এক প্রচার। প্রচারের উদ্দেশ্য মানুষকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রস্তুত করে তোলা।”
গ্রীক মহাকবি হোমারের ওরাল এপিক বা মুখে রচিত মহাকাব্য ছিল ‘ওডিসি’ (Odyssey)। চব্বিশ অধ্যায়ের মহাকাব্য। আরেক বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য ‘ইলিয়াড’ এর পরিশিষ্ট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ইউলিসিস বা অডিসিউস ট্রয়ের যুদ্ধে অংশ নেন। তাঁর স্বদেশ যাত্রা নিয়ে রচিত এই মহাকাব্য খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকের। ওটাতে সম্রাট ইউলিসিস অতিমানবিক সংগ্রাম করেছে নিজ দেশ তথা লক্ষ্যে পৌঁছুতে। এর পর আরো একটা বইয়ের নামে ওডিসি এসেছে। এটার এ নামকরণের কারণ ওডিসির মতোই লক্ষ্যের দুস্তরতা আরোপ করা। টু থাউজ্যান্ড ওয়ান: এ স্পেস ওডিসি’ (2001: A Space Odyssey)। উনিশশো আটষট্টি সালে বেরুনোর পর আণবিক বোমার চেয়ে কোনো অংশে কম শক্তির বিস্ফোরণ ঘটায়নি সায়েন্স ফিকশন বোদ্ধাদের মনোজগতে। একজন পরিপূর্ণ দার্শনিকের রূপ পরিগ্রহণ করেন ক্লার্ক এতে। বলা হয় এজন্যই সবচে বেশি পরিচিত তিনি।
এটাকে অনেকে বলেন মহাকাশ বিজ্ঞান বিষয়ক সায়েন্স ফিকশনগুলোর-বিশেষ করে মহাকাশ অভিযান বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের কম্পাস হিসেবে। কারণ তিনি এতে মহাকাশ অভিযানের সব দিক তথা প্রযুক্তি আর মানবিকতা-দুইই প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীর মতো। স্টার ট্রেক’ থেকে ‘মার্স অ্যাটাক’ পর্যন্ত এর প্রভাব পড়েছে। এমনকি ক্লার্কের ওডিসি পেন্টালজিকে মহাকাশভিত্তিক সায়েন্স ফিকশনের প্রথম বিস্তৃত মাইল ফলক বলা হয়। এ অসম্ভব সফল বইটির আরেক অংশ লেখেন ‘টু থাউজ্যান্ড টেন: ওডিসি টু’। এরপর ‘টু থাউজ্যান্ড সিক্সটি ওয়ান: ওডিসি থ্রি’। কোনোটি লেখার সময়ই ইচ্ছা ছিলো না আরো একটু প্রলম্বিত করার। কিন্তু পাঠকরা ছাড়েননি ক্লার্ককে। আর কালাতিক্রমী অনন্যসাধারণ ঘটনাচক্র বাধ্য করেছে আরেকটি লিখে ওডিসির পাট চুকিয়ে দিতে। সময় সমাজ আর ভাবনাকে ডিঙিয়ে গিয়ে এ মহাকাব্যের সমাপ্তি টানলেন ‘থ্রি থাউজ্যান্ড ওয়ান: দ্য ফাইনাল ওডিসি’ নামে। এর মাধ্যমেই ওডিসি রহস্যের দুদিকের ভারি দরোজা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিতে চান উনিশশো সাতানব্বইতে। কিন্তু বিধি বাম, পাঠক-প্রকাশক সম্পাদকরা তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুললে বাধ্য হন ‘ওডিসি ফাইভ’ লিখতে। ক’দিন আগে শেষ করেছেন বইটা। হয়তো বেঁচে থাকলে সব সময়ই তাকে ওডিসি লিখে যেতে হবে মানুষের চাপে পড়ে।
এর রহস্যঘেরা টোটেম, কু, হাল-ন হাজার কম্পিউটার, মানবিক দ্বন্দ্ব-কোনোটার চেয়ে কোনোটা কম যায় না। এক্সপেডিশন অফ আর্থ’ (১৯৫৩) এর বিশেষ একটা ছোটগল্প ‘দ্য সেন্টিনেল’। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ‘দ্য সেন্টিনেল কে পরে ওডিসির সিনেমা স্ক্রিপ্টে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা মানিয়েও গেছে। এ নিয়ে লেখা চিত্রনাট্য ওই বছরের সেরার মর্যাদা কেড়ে আনে। একাডেমিক অ্যাওয়ার্ড ফর স্পেশাল ভিজুয়্যাল ইফেক্টস’ এবং ব্রিটিশ ফিল্ম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস ফর বেস্ট সিনেমেটোগ্রাফি, বেস্ট সাউন্ড, বেস্ট আর্ট ডিরেকশন’ পায়। অস্কার অ্যাওয়ার্ডের মনোনয়নও পেয়েছে ওটা। সবচে বড় কথা, ‘অল টাইম বেস্ট সায়েন্স ফিকশন মুভি’, ‘মোস্ট ওয়াইডলি ডিসকাসড এস এফ মুভি অব অল টাইম উপাধি পায় ওটি।
ক্লার্কের জাদুর সাথে কুবরিকের পরিচালনায় সৃষ্ট অমর গাঁথার ছবিটা মুক্তি পায় উনিশশো আটষট্টিতে। অবাক ব্যাপার, এর গ্রাফিক্যাল কাজ দেখে কেউ বলবে না এটা এত আগের। আর খারাপ দিক হচ্ছে-একেকটা দৃশ্য অনেক অনেক বেশি লম্বা এবং কাহিনীকে বেশ বদলে দেয়া হয়েছে ছবিতে। চার বছর আগে প্রয়াত বিখ্যাত চিত্র পরিচালক স্ট্যানলি কুবরিক ঘটনাটা নিয়েছিলেন। এ ছবি এত বেশি প্রভাব। ফেলেছে বাস্তব ক্ষেত্রে-যা এক কথায় অবিশ্বাস্য।
ইসরায়েলী কম্পিউটার সংস্থা বহুদিন ধরে গবেষণা চালাচ্ছে শুনে শেখা কম্পিউটার বিষয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে তারা তাদের কম্পিউটারের নাম রেখেছে ‘হাল’! এর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (A.I) বিষয়ক অগ্রগতিরও দাবী করছে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা তাদের সর্বশেষ মহাকাশযানের নাম রেখেছে ‘ওডিসি’। রুশ বিজ্ঞানীরা শুনে শেখা কম্পিউটার তৈরির ব্যাপারে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছুবার ঘোষণা দিচ্ছেন।
বহুদেশে ‘আর্থার সি ক্লার্কের রহস্যময় জগৎ’ টিভি সিরিয়ালটি চলছে। ওটা তের পর্বের।
ছোটগল্পের মাঝে ‘দ্য সেন্টিনেল’, ‘হুজ দেয়ার হলো ক্লার্কের নিজ রীতির খাঁটি ভয়ভিত্তিক সায়েন্স ফিকশন। প্রতীক্ষা’, ‘সময় সমস্যা’, ‘অস্ত্র প্রতিযোগিতা’, ‘অন্ধকারের পথ’ তাঁর কয়েকটি অনন্য কর্ম।
তাঁর আরেক চরিত্র রামা’। লিখেছেন গার্ডেন অব রামা’, ‘রামা দ্য সেকেন্ড, ‘রামা রিভিড সায়েন্স ফিকশনের উপন্যাসগুলো। মজার ব্যাপার হলো, অনেক বোদ্ধা মনে করেন ক্লার্কের শ্রেষ্ঠ কাজ ওডিসির সিরিজ নয় বরং রামার সিরিজ। এটা পুরস্কারও পেয়েছে বড় বড়। কিন্তু প্রভাব ফেলতে পারেনি ওডিসির মতো।
‘চাইল্ডহুডস এন্ড’ বিখ্যাত বই। লিখেছেন ‘দ্য লাইট অব দ্য আদার ডে’জ’। বহু নন ফিকশনও লিখেছেন তিনি। লেখার ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ছিল সেই মহাকাশ ভ্রমণ, সমুদ্রগর্ভের অতলে হারিয়ে যাওয়ার আলোচনার আশেপাশেই।
সায়েন্স ফিকশন ও ভবিষ্যৎ জীবনে মানুষকে যে সমস্যাটার মোকাবিলা করতে হয় তা হল ভয়। সম্ভবত মানবের আদিমতম শত্রু এবং অসহায়ত্বের প্রথম প্রতীক। তিনি তাঁর রচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন পাঁচটা বিষয়ে যা সাহিত্যগুণকে মহিমান্বিত করেছে। এক, ভয়; দুই. মানবিকতা বিশ্লেষণ; তিন, মানসিকতা বিশ্লেষণ; চার. অনিশ্চয়তায় ভরা কাহিনীর ধারা আর গঠনগত দিকেও অনিশ্চয়তা; পাঁচ, কাহিনীর বক।
বিজ্ঞানের দিক দিয়ে কখন কী প্রাধান্য দিয়েছেন তা কোনো ছকে ফেলে দেয়া সম্ভব না; তবে সাধারণত যা উঠে আসে তা হচ্ছে, ১.স্পেস ট্রাভেল কেন্দ্র করে অনেক কাহিনীই ঘুরেছে, তিনি মূলত একজন মহাকাশবিদ্যার এস এফ লেখক; ২.সরাসরি সংযোগে না এসেও সবচে বড় প্রভাবটা ফেলে এলিয়েনই; ৩.স্বাভাবিকভাবেই নতুন গ্রহ বা উপগ্রহের উপর কাহিনী ঘুরপাক খায় প্রচণ্ড গতিতে; ৪. মহাকাশ বসত বা মহাকাশ যুগে মানব বসতি বিষয়ে অহরহ উঠে আসে ঘটনা। এক কথায়, তিনি অনন্ত নক্ষত্রবীথির কথক।
তাঁর লেখা যে মহাকাশ অভিযান, মহাকাশ টেকনোলজি নিয়ে আবর্তিত হয়, তা বেশ কয়েকবার বিভিন্ন লেখক বলেছেন। বিচারটা অনেক বেশি স্কুল হয়ে গেলেও করার কিছু নেই। তাঁর মতো লেখক বিজ্ঞানের কোনো দিক নিয়ে কাজ করছেন তা বিশ্লেষণ করাটা প্রায় অসম্ভব যেখানে বিজ্ঞানের ভোলা মাঠের পুরোটাতেই তিনি ম্যারাডোনা। তার আরেক ব্যাপার ভাল লাগে, আর সব ইংরেজ বা আমেরিকান লেখকের মতো শুধু ইংরেজ চরিত্র রাখেন না লেখাগুলোয়। বরং আফ্রিকান, ভারতীয়, চৈনিক, রাশিয়ান চরিত্র অনেক। কারণ তিনি কোনো জাতি বা দেশের প্রতিনিধি নন, প্রতিনিধি এ বিশ্বের মানুষের।
আর সাইবার পাঙ্ক হিসেবে তাঁকে কোনো শ্রেণীতে ফেলে দেয়া কঠিন। কারণ সাইবার পাঙ্ক শ্রেণীর জন্মের বহু আগ থেকেই তিনি নক্ষত্র। তবে লেখায় কাব্যধর্মীতা, উপমাশ্রয়, লম্বা বাক্য লেখার প্রবণতা, বক্র বচন, একটা বিষয় নিয়ে বেশি ঘাটানো আর বহু তুলনা করার স্টাইল থাকার কারণে অবশ্যই তাঁকে সাইবার পাঙ্ক লেখক বলা যায় না। কারণ তার সেসব বৈশিষ্ট্য ষাট-সতুর দশকে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের। এসব বৈশিষ্ট্য অনেকটাই বিরক্ত করে পাঠককে, কিন্তু তিনি সেসময় সে স্টাইলেইতো লিখবেন, এটাই স্বাভাবিক। আর সাইবার পাঙ্ক হল আশির শেষার্ধে শুরু হওয়া একটা ধারা যা সাহিত্যকে গোয় ধরে না।
রাশিয়ায় ইউটোপিয়ান ফিকশন (utopian fiction) বা স্বপ্ন রাজ্যের গল্প নামে একটা ধারা বেশ পুরনো আমল থেকেই প্রচলিত। এর গোড়া অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝিতে দেবে আছে। একে অনেকে কম্যুনিস্ট ফিকশনও বলেন। এক মতে, ইউটোপিয়ার অর্থ দাঁড়ায় ভবিষ্যতের স্থানিক রূপ বা ভবিষ্যৎকে একটি সুন্দর স্থান হিসেবে কল্পনা করা। আরেক মতানুসারে, এর অর্থ ‘স্বপ্নীল জগৎ’। সত্যি বলতে গেলে, ক্লার্কের গোটা লেখার কোথাও এই স্বপ্ন রাজ্যের পেছনে দৌড়ানো দেখা যায়নি। তবে ভিতরে এমন একটা প্রবাহ দেখা যায়। আবার তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান ওডিসি পেন্টালজিতে এই ‘স্টার চাইল্ড’ এর পেছনে ধাওয়া করাটাই দেখানো হয়েছে যা আসলে ইউটোপিয়ান। কিন্তু ক্লার্ক কোন শ্রেণীর? আমার মনে হয় ক্লার্ককে সেমি সাইবারপাঙ্ক আর টেকনো ইউটোপিয়ান বলা যায়। কারণ প্রাযুক্তিক ইউটোপিয়া বা টেকননা ইউটোপিয়ান প্রভাবই তাঁর লেখায় বেশি।
অনেকটা স্পষ্টভাবে ঘটনা বুঝিয়ে দেন পাঠককে অত্যন্ত শক্তিময় আবেদনের সাহায্যে। তাতেই পাঠক পেয়ে যায় অসাধারণ মজা। তাঁর দারুণ একটি বৈশিষ্ট্য-পাঠককে খোলাসা করে বলেও দেন, রাখেন রহস্যও। তিনি আসিমভের মতো পাঠকের উপর সিদ্ধান্ত ঠিকই ছাড়েন, তবে আসিমভের চেয়ে আরেকটু এগিয়ে নেন কাহিনী। এতে করে পাঠককে কষ্ট করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় না, অবশ্যম্ভাবীরূপে তা এসে যায়। আর গদ্য অন্তর্গত ধোঁয়াশার দিক দিয়ে আসিমভের চেয়ে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠতে দেন কাহিনীকে। তবে ক্লার্কের গদ্যশৈলী থেকে আসিমভের শৈলী অনেক সরল আর সুখপাঠ্য। থ্রিলার ভাবটা ফোঁটানোর ক্ষেত্রেও আসিমভ অগ্রগণ্য। ঠিক আসিমভের মতোই বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উভয়ক্ষেত্রেই সমান দৃষ্টি রেখে প্রকাশিত করেন ঘটনা। জুলভার্নের বেলায় একটা বইয়ের পাতাগুলোর মতো মনে হয় এ পাতা উল্টালেই বই শেষ-অর্থাৎ আপাতত কাহিনী এক ধারায়, রহস্য এক ধারায়-পরের মুহূর্তেই ওটার একটা জট খুলে যাওয়ায় পরের আরেক রহস্য ধরা দেয় এবং বেশ কবার এমন হবার পর কাহিনী শেষ হয়। ক্লার্কও প্রায় একই প্রক্রিয়ায় এখোন। তবে পার্থক্য হচ্ছে, ভার্নের ধাপ ও কাহিনী স্বচ্ছতম, ক্লার্কেরটা এই একটু কম স্বচ্ছ। ধাপও-কাহিনীও।
বিখ্যাত আরেক থ্রি ল’জ দিয়েছেন তিনি। বলেছেন কালোত্তীর্ণ কথা ‘যখন একজন একনিষ্ঠ আর পুরনো বিজ্ঞানী ঘোষণা করেন যে, কিছু একটা সম্ভব, তিনি বলছেন একেবারে ঠিক কথা। যখন তিনি বলেন যে কিছু একটা অসম্ভব, খুব সম্ভবত তিনিই এবার ভুল করছেন।’
বয়স হয়ে গেছে। লিখেছেন একটা বড়সড় বই স্টিফেন বাক্সটারের সাথে। তবে তিনি থেমে নেই। এখনো প্রথম যৌবনের মতো সাগরে ডাইভ দিতে চান। পাঞ্জায় হারাতে চান পঁচিশ বছরের যুবককে। এজন্যই হয়তো তিনি সায়েন্স ফিকশন কাহিনীকার-চির তারুণ্যের সবুজ পাতায় আবৃত। সময় তাঁর এ দুর্বল অবস্থাকে আরো দুর্বল করে দিতে পারে। ক্লার্ক থেকেই যাবেন-যেমন থেকে গেছেন আসিমভ-জুলভার্নরা।
নির্ঘণ্ট
১. চারপেয়ে সরীসৃপ: প্রাচীন চারপেয়ে সরীসৃপ মানে ডায়নোসর জাতীয় প্রাণী।
২. জিন প্রাণীর প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে থাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম, প্রতিটি ক্রোমোজোমে বংশগতির বার্তাবাহক যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ থাকে তা জিন। চোখের রঙ, গায়ের উচ্চতা, লোমশতা-এমন প্রতিটি বিষয় প্রকাশের জন্য এক বা একাধিক জিন কাজ করে। জিনের জন্যই বাবা-মায়ের বৈশিষ্ট্য সন্তানের দিকে যায়। মজার ব্যাপার হল, দাদার লাল চুল এবং বাবার কালো চুল হলেও নাতির লাল চুল হতে পারে, অর্থাৎ মানুষের জিন হারায় না, পরের কোনো না কোনো বংশধরের কাছে প্রকাশ পেতে পারে। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে গবেষণায় বিজ্ঞানীরা মানুষের মাত্র ৪% জিনের কাজ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন। জিন গবেষণা শেষ হলে মানুষের অমর হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।
৩. প্লেইস্টোসিন: এক ভূতাত্ত্বিক, আবহাওয়া নির্ভর যুগ। চব্বিশ লক্ষ বছর আগের। এর পর বরফ যুগ। প্লায়োসিন-প্লেইস্টোসিন থেকেই মানব জাতির উদ্ভব (বিবর্তন মতবাদ অনুসারে)। ইউরোপ-আমেরিকায় বর্তমান মাটি এবং বহু বিলুপ্ত প্রজাতির ফসিল এ উষ্ণ যুগের ফসল।
৪. ডায়নোথেরিয়া: হাতি জাতীয় বিশাল স্থলজ প্রাণীর উপগোত্র। পূর্বসূরী ম্যামথ, উলি ম্যামথ।
৫. শব্দেতর: যে নিচু কম্পাঙ্কের শব্দ শোনা যায় না। মানুষ আঠারো হার্জের নিচের কম্পাঙ্কের শব্দ শোনে না। আবার আঠারো হাজার হার্জের উপরের শব্দও শোনে না। সেটা শব্দোত্তর তরঙ্গ।
৬. অ্যান্টিলোপ: দ্রুতগামী, হাল্কাপাতলা, তৃণভোজী, বিচরণশীল প্রাণীর দল। ভেড়া ও ছাগলজাতীয় প্রাচীন প্রাণী।
৭. ইউটোপিয়া: কল্পরাজ্য, কল্প-ভূস্বর্গ, পৃথিবীর সর্বসুখের স্থান। টমাস মুর তার ইউটোপিয়া গ্রন্থে প্রথম এ নাম দেন। তাঁর কল্পিত এই দ্বীপে আসলে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করেছেন। অনেকে মনে করেন সায়েন্স ফিকশন মানে ইউটোপিয়ার সন্ধান। তাই এস, এফ. এ ইউটোপিয়ান ও এন্টি ইউটোপিয়ান ধারা চালু হয়েছে।
৮. গাইডেড মিসাইল: নিক্ষেপের পর যে ক্ষেপণাস্ত্রের দিক বদলানো যায়। অটো গাইডেড মিসাইল আবার শক্রযানের পেছনে ধোয়া অথবা তাপ অনুসরণ করে যেতেই থাকে।
৯. গ্যানট্রি: যে বিশাল প্ল্যাটফর্ম থেকে রকেট বা অন্য মহাকাশযান ছোঁড়া হয়।
১০. ওয়্যারহেড: মিসাইলের অগ্রভাগে আসল বিস্ফোরক থাকলে সেটা। এখানে পারমাণবিক বোমা যা মিসাইলে বসানো যাবে।
১১. কেনেডি: জন ফ্রিৎজেরাল্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট, কিউবা ও বার্লিন সংকটের ত্রাতা। উনিশশো তেষট্টি সালে খোলা গাড়িতে যাবার সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত। পৃথিবীর সবচে বড় স্পেস স্টেশনটি কেনেডির নামে।
১২. জি: সপ্তদশ শতকে ইম্পার শব্দটি ব্যবহার করেন ডানে চলা বা সামনে যাওয়া বোঝাতে। পরে শব্দটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে। এখানে টু জি মানে মাধ্যাকর্ষণের দ্বিগুণ।
১৩. সিস্টেম: কোনো পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। যেমন হার্ড ডিস্ক, মনিটর, স্পিকার প্রতিটি যন্ত্র হলেও কম্পিউটার একটি যন্ত্র নয়, বরং যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বা সিস্টেম।
১৪. গোল্ড কোস্ট: গিনি উপসাগরের উপকূলীয় এলাকা, স্বর্ণ পাওয়া যেত, ব্রিটিশ শাসনে গোল্ড কোস্ট কলোনি নামে যে এলাকা ছিল পরে তা ঘানা নামে স্বাধীন হয়।
১৫. রেডিও অবজার্ভেটরি: প্রাকৃতিক ব্যাপার নিরীক্ষণের বিল্ডিং বা প্রতিষ্ঠান, যা দূরের ব্যাপার ও তরঙ্গ যোগাযোগ পরীক্ষা করে।
১৬. কক্সটন: উইলিয়াম। প্রথম ইংরেজ ছাপাকর্মি, প্রকাশক, অনুবাদক। গুটেনবার্গের সমসাময়িক। এক হিসাবে প্রকাশনা শিল্পের সার্থক সর্বচারী জনক।
১৭. গুটেনবার্গ: জোহান্স,। ১৪৩৬ সালে ছাপাখানার আবিষ্কারক / উন্নয়নকারী। বিয়াল্লিশ লাইন বা মাজারিন বাইবেলের অপর নাম তাঁর নামে, গুটেনবার্গ বাইবেল।
১৮. ইথার: আগে ধরা হত মহাশূন্যে ইথার একটি অতি স্থিতিস্থাপক মাধ্যম। কারণ ধরা হতো যে আলো একটি তরঙ্গ। বাস্তবে কোনো তরঙ্গই মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে না। তাই ইথারের কল্পনা। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব আসার পর ধারণা পাল্টে যায়। বর্তমানে শব্দটিকে সম্মান করার জন্য এক যৌগকে এ নাম দেয়া হয়েছে।
১৯. বালি: জাভার এক মাইল দূরের ইন্দোনেশীয় পাথুরে পর্যটন দ্বীপ। সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নামও বালি। প্রকৃতি অনিন্দ্যসুন্দর। দানবীয় সব বটগাছ, বাঘ (এর মধ্যে বালি বাঘ, রয়েল বেঙ্গলের মতো দেখতে, বিলুপ্ত), হাজারও হরিণ আর বুনো শুয়োর আছে। অবকাশ যাপন কেন্দ্র ও পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠার পর ক্লার্কের স্বপ্নের বালি দ্বীপ আসলেই কলুষিত হয়েছে,তারপর সেখানে অস্ট্রেলিয় পর্যটকদের উপর বোমাও বিস্ফোরিত হয় এবং ইমাম সমুদ্র অভিযুক্ত হন।
২০. এ্যালগিঃ এক ইঞ্চির আড়াই হাজার ভাগের একভাগ থেকে শুরু করে দু’শ ফুট পর্যন্ত দৈর্ঘের বিচিত্র সব জলজ আলো-খাদক শৈবাল-শ্যাওলার দল। এরা আমাদের অক্সিজেনের এক বিরাট অংশ দেয় এবং সব জলজ প্রাণীর প্রাথমিক খাদ্য।
২১. ক্ল্যাস্ট্রোফোবিয়া: এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা। আবদ্ধ স্থানে অস্বস্তি বোধ বা ভয়/ আতঙ্ক বোধ।
২২. কোর (কর্প): সৈন্যদলের সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ যা সাধারণত একই কাজ করে। সাধরণত আশি হাজার সেনার ইউনিট, এর প্রধান একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। যেমন: ক্যাডেট কোর, পদাতিক কোর। তবে বেসামরিক ক্ষেত্রে এক অভিন্ন ও বিশাল কাজে অংশ নেয়া লোকবলকে কোর বলা যায়।
২৩. লক্স: লিকুইড অক্সিজেন। উনিশশো তেইশ সালে এই সংক্ষিপ্ত নাম দেয়া হয়।
২৪. পোব: ছোট কিন্তু তথ্য সংগ্রহকারী বা অভিযান চালনাকারী যন্ত্র। আবার পরীক্ষা করলেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। সনিক প্রোব মানে শব্দের তরঙ্গ দিয়ে চেষ্টা করা।
২৫. নিউট্রন বীম: হাইড্রোজেন ছাড়া আর সব পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন আছে, ভর প্রায় প্রোটনের সমান। আবিস্কৃত হয় উনিশশো বত্রিশে। এর কোনো চার্জ নেই, তাই আকৃষ্ট বা বিকর্ষিত হয় না। বেশি ভর ও চার্জহীনতার কারণে নিউট্রনের সরল প্রবাহ বা বিম চালানো শক্তিশালী কিন্তু নিরাপদ ও নিশ্চিত।
২৬. প্যানডোরার বাক্স: গ্রিক পুরাণ অনুসারে প্রথম নারী, তাকে সব দেবতা তাদের পছন্দের রূপ দিয়ে গড়ে পৃথিবীতে পাঠান একটা বাক্স দিয়ে যেটা খোলা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অনেক পেয়ে প্যানডোরা লোভী হয়ে বাক্সটা খুলে ফেলেই সর্বনাশ ডেকে আনে। প্রাকৃতিক-অতিপ্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে।
২৭. প্যাস্কেল: ব্লেইজ.। প্রখ্যাত কিশোর গণিতজ্ঞ। ১৯ বছর বয়সেই ‘প্যাস্কেলের চাকা’ বানান। কম্পিউটার বিজ্ঞান ও গণিতে এর অনেক অবদান। অন্য কীর্তিও রয়েছে।
২৮. ক্যানবেরা: সিডনির দেড়শো মাইল দূরে, মলোঙ্গো নদী তীরে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী।
২৯. অ্যামনেসিয়া: চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্মৃতিভ্রষ্টতা।
৩০. কম্পিউটার প্রজন্ম: ক্লার্ক তিনটি প্রজন্ম দেখিয়েছিলেন কারণ চৌষট্টি পর্যন্ত বিশ বছর অঙর কম্পিউটারের প্রজন্ম এগিয়ে আসত। কিন্তু একাত্তরে মাইক্রো প্রসেসর আবিষ্কারের পর ধারাটা পাল্টে যায়। আমরা কম্পিউটারের পঞ্চম প্রজন্মের দ্বারপ্রান্তে আছি।
৩১. এনিয়াক: ইলেক্ট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেটর অ্যান্ড কম্পিউটার। এটিই প্রথম প্রোগ্রাম ঢোকানোর মতো ডিজিটাল কম্পিউটার। এ থেকেই প্রজন্ম শুরু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তালে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনী একটি পুরোপুরি ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার নির্মাণের পরিকল্পনা নিলে আধুনিক কম্পিউটারের জনক জন ভন নিউম্যান, প্রেসপার একটি জুনিয়র এবং হারম্যান গোল্ডস্টেইনের মতো কম্পিউটার মহারথী ও মুর স্কুল অব ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেয়। পঞ্চাশ ফুট বাই ত্রিশ ফুটের ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে চল্লিশজন বিজ্ঞানী তিন দেয়ালজুড়ে থাকা এ কম্পিউটার চালাতেন। অনেকেই জানেন না, মানবজাতির উপর আশীর্বাদ কম্পিউটারের শুরু এনিয়াক আসলে তৈরি করা হচ্ছিল হাইড্রোজেন বোমা বানানোর হিসাব করার জন্যে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তিন বছরের চেষ্টায় চার লাখ ডলার ব্যয়ে উনিশশো চল্লিশের ফেব্রুয়ারীতে যখন এ জিনিস তৈরি হয় তখন যুদ্ধই শেষ।
৩২. সলিড স্টেট মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স: একেবারে আণবিক স্তরে নেমে গিয়ে কঠিন পদার্থের ইলেক্ট্রিক যন্ত্র তৈরির প্রচেষ্টার বিজ্ঞান।
৩৩. মিনস্কি: মারভিন,। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তত্ত্বের দিকপাল। ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকননালজির (এম আই টি) নিউরোফিজিওলজি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ল্যাবরেটরির সাবেক শিক্ষক। শত শত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশারদের দীক্ষাগুরু এবং বাস্তব গবেষক। তিনি এজন্য প্রচুর কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্র তৈরি ও উদ্ভাবন করেন।
৩৪. নিউরাল নেটওয়ার্ক: ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন নিউরন কোষ জটিলভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত না হয়ে মানুষের মস্তিষ্ক গঠন করে। তাই এই জটিলতার বিশালত্ব ও কাজের ব্যাপকতাকে বোঝাতে কথাটা ব্যবহৃত হয় ভবিষ্যৎ কম্পিউটারের ক্ষেত্রে। অনেকে এ দিয়ে মানবীয় গুণের কম্পিউটারের কথাও বোঝান।
৩৫. পাইথিয়াস: প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম হ্যাঁলিকারনাসাসের সমাধিমন্দির নির্মিত হয় যীশুর জন্মের সাড়ে তিনশো বছর আগে। তিনি স্থপতি।
৩৬. গ্যালিয়ন: বিশাল স্প্যানিশ শিপ। মূলত সাঁজোয়া যুদ্ধে ব্যবহার হতো পনের থেকে আঠারো শতকে।
৩৭. কুক: রবিন.। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী।
৩৮. রজার: গ্রহণ করা হয়েছে, শুনতে পেয়েছি। শব্দটা শুধু রেডিও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সব দেশে ব্যবহার করা হয়।
৩৯. হাইপোকন্দ্রিয়া: স্বাস্থ্য বা রোগ নিয়ে মনে ভয় পুষে রাখার রোগ। আবার পুরো পেটের উপরদিকের অংশকেও বোঝায়।
৪০. বিস্ফোরণ: মানুষের শরীরে গ্যাসীয় অনুগুলো তরল আছে কিছুটা চাপ ও তাপের কারণে। সব সময় বায়ুমণ্ডল আমাদের উপর অত্যন্ত বেশি চাপ দেয় এবং পৃথিবী আকর্ষণ করে বলে শরীরের দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বনডাইঅক্সাইডসহ আরো শত গ্যাস তরল হয়ে থাকে। কিম্বা গ্যাসীয় থাকলেও কম স্থান দখল করে। কিন্তু যেখানে এক বিন্দুও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ নেই সেখানে সাথে সাথে সেসব তরল ও সংকুচিত বায়বীয় গ্যাস তাদের গ্যাসীয় রূপ পাবার জন্য বিস্তৃত হয়, ফলে মহাকাশে কোনো স্পেসস্যুট পরা না থাকলে প্রাণীদেহ একেবারে ফেটে যায়।
৪১. নিউরোসিস: নিউরনে গণ্ডগোল। আসলে হাল্কা মানসিক রোগকে বোঝায় যার ফলে বাহ্যিক কথাবার্তায় এবং আচরণে বোঝা যায় না। অপ্রকাশ্য পাগলামি।
৪২. এইচ জি ওয়েলস: হার্বার্ট জর্জ,। ভার্ন, আসিমভ, ক্লার্কের পর সবচে দামী এবং সাড়া জাগানো সায়েন্স ফিকশন লেখক। প্রথম জীবনে অর্থাভাবে নানা কাজ করেছেন অথচ পরে তাঁর লেখা কোটি কোটি মানুষ পড়ে। ‘দি টাইম মেশিন’, ‘দ্য ইনভিজিবল ম্যান’ তাঁর অমর কীর্তি।
৪৩. আতঙ্ক: আমেরিকার মানুষ মঙ্গল নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগার সময় এক হ্যালোইন উৎসবের রাতে (যে রাতে ছোটরা ছদ্মবেশে মানুষের বাড়ি বেড়াতে যায়) ওয়েলসের এক সায়েন্স ফিকশনের নাট্যরূপ রেডিওতে প্রচারের সময় নাটকের মধ্যে খবরে বলা হচ্ছিল যে মঙ্গলের প্রাণীরা মানুষের উপর আক্রমণ করেছে। কিন্তু অনেকে সে সময় রেডিও খোলে এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অর্থ শতাব্দী আগেও মানুষ এত বিজ্ঞান সচেতন এবং এস এফে বিশ্বাসী ছিল যে সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাঁচার তাগিদে পথে নেমে পড়ে, অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়, লুকিয়ে পড়ে পথেঘাটে, কেননা হ্যালোইনে আসলেই ছদ্মবেশে আসা খুব সহজ কাজ। সেই রাতের মতো আতঙ্ক মানুষের মনে খুব কমই নেমেছে।
৪৪. মিল্কি ওয়ে: আমাদের গ্যালাক্সি হলেও আমরা এর প্রান্তে পড়ে আছি বলে একে দেখতে পাই। দশ হাজার কোটির উপর নক্ষত্র সর্পিল পথে পানির ঘূর্ণির মতো একত্র হয়ে এ নীহারিকা সৃষ্টি করেছে।
৪৫. আলফা সেন্টোরি: সৌরজগতের সবচে কাছের জগৎ, ত্রি-সূর্য। সবচে কাছেরটার নাম প্রক্সিমা সেন্টোরি। আলো যেতে ৪.৩ বছর সময় প্রয়োজন। সেঞ্চুরি (শতক) বলা হয় মাঝে মাঝে, সেটা ভুল। সেন্টোরি বা সেন্টাউরি অর্থ পুরনো পৃথিবীর গাছ।
৪৬. নিলস বোর: অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। ডেনিশ পদার্থবিদ নিলস হেনরিক ডেভিড বোর প্রথম কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগকারী, পরমাণুর শক্তির ব্যাখ্যাদানকারী। আসলে পরমাণু কেমন-তা নিয়েই গণ্ডগোল চলছিল, সেটার আংশিক সমাধান দিয়ে বোরের পরমাণু মডেল গড়েন একেবারে তরুণ থাকাকালে। আণবিক নিউক্লিয়াসের তরল মডেল তৈরি করেন। উনিশশো বাইশে পদার্থে নোবেল পান। তিনি নাৎসী বিরোধী আন্দোলনেও ছিলেন। পারমাণবিক বোমাবিরোধী প্রচারণার জন্য উনিশশো সাতান্নতে শান্তি পুরস্কারও পান। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবদান ছিল।
৪৭. সিমবায়োসিস: দুই ভিন্ন সত্তা বা প্রাণীর একত্রে বসবাস। মনের স্ববিরোধিতা।
৪৮. শ’: দরিদ্র মায়ের উপর নির্ভরশীল হতে না চাওয়া এক তরুণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়ে সময় কাটায় এবং লেখে। উপন্যাসগুলি চরমভাবে ব্যর্থ হয়, প্রকাশই করে না কেউ। পরে সে হয় সমাজবাদী একজন নাট্যকার এবং সমালোচক। তার নাটক জনপ্রিয় হতে সময় লাগে, অথচ তিনি নোবেল নেননি, জীবন্ত কিংবদন্তী হয়ে ছিলেন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান’ এর স্রষ্টা খুব রসিকও ছিলেন। একবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেয়ার সময় এক মহিলা অন্যজনকে বলছিলেন যে জর্জ বার্নার্ড শয়ের মতো লোকের প্যান্ট টেনে টেনে তোলা উচিত নয়। শ’ জবাবে বলেছিলেন যে প্যান্টটাকে নেমে পড়তে দেয়াও তাঁর উচিত মনে হচ্ছে না।
৪৯. ইবসেন: হেনরিক জন.। শ্রেষ্ঠ নরওয়েজিয়ান নাট্যকার। তাঁর নাটকও এত কম চলেছিল যে তিনি নাটক ছেড়ে দেয়ার কথাও ভেবেছেন।
৫০. ভার্দি: গুইসেপো ফচুনেনো ফ্রান্সিসকো,। উনিশ শতকের ইতালীয় অপেরার শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।
৫১. বিথোফেন: লুডউইক ভন.। ঊনবিংশ শতাব্দীর জগৎবিখ্যাত জার্মান সুরস্রষ্টা। নটি পর্যন্ত সিম্ফনির কথা শোনা যায়। পঞ্চম সিম্ফনিটি পৃথিবীর সব মানুষ কোনো না। কোনোভাবে শুনেছে। ঘড়ি, মোবাইল ফোন, খেলনা, কলিং বেল বা মিউজিক কালেকশন-সব ক্ষেত্রে তাঁর এই অমর সৃষ্টি বেজে ওঠে। বলা হয় তিনি কোনোদিন কানে শোনেননি।
৫২. বাচ: জন ক্রিস্টোফ ফ্রেডরিক.। অষ্টাদশ শতকের সুর-নির্দেশক, সিম্ফনি-নির্মাতা বাচ প্রথমে এক জমিদারের বাদ্যবাদক ছিলেন। অর্কেস্ট্রা, পিয়ানোসহ নানা যন্ত্রে নতুন সুর তুলেছেন।
বিশেষ টিকা : ভ্যান অ্যালেন : আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী। তরুণ বয়সে পৃথিবী ঘিরে রাখা বলয় আবিষ্কার করে পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী। এ বেল্ট খুব প্রভাবশালী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকায় তাঁর সাথে ডিনারে যাবার আগে তার কোমরবন্ধনী জড়িয়ে বলেছিলেন, ‘ভ্যান অ্যালেনের বেল্ট আমার কোমরে।’